আগের কথা
সতেরো শো সাতান্ন সাল।
মীর জাফরদের চক্রান্তে ইংরেজদের কাছে পরাজিত হলেন বাংলার নবাব সিরাজদ্দৌলাহ।
পলাশীর প্রান্তরে নবাব সিরাজদ্দৌলার পরাজয়ের পর বাংলার মুসলমানদের ভাগ্যাকাশে দেখা দেয় এক ভয়ংকর সর্বনাশের ঘনঘটা।
ইংরেজ এবং উগ্র হিন্দুদের হাতে জিম্মি হয়ে পড়ে বাংলার মুসলমান। রাজনৈতিক, ঐতিহ্যিক এবং সাস্কৃতিক ক্ষেত্রে মুসলমানরা এ সময়ে যেমন ইবংরেজ ও হিন্দুদের উৎপীড়নের শিকার হয়, তেমনি তাদের নির্মমতার শিকার হয়ে অর্থনৈতিকভাবে তারা দুর্বল ও নিঃস্ব হয়ে পড়ে।
মুর্শিদকুলী খানের আমল থেকেই হিন্দুরা মুসলিম শাসন উৎখাত করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলো। ইংরেজ ব্যবসায়ীদের সাথে তাদের সম্পর্ক ছিলো অত্যন্ত নিবিড়।
সতেরো শো ছত্রিশ সাল থেকে সতেরো শো চল্লিশ সালের মধ্যে ইংরেজ কোম্পানী- কলকাতায় বায়ান্নজন ব্যবসায়ী নিয়োগ করেছিলেন। তাদের সবাই ছিলো হিন্দু। সতেরো শো ঊনচল্লিশ সালে কাশিম বাজারে তারা পঁচিশজন ব্যবসায়ী নিয়োগ করে। তারাও ছিলো হিন্দু।
এ সময়ে মুসলমানদের কোথাও স্থান ছিলো না। না ব্যবসায় বাণিজ্যের ক্ষেত্রে। না চাকরীর ক্ষেত্রে। যাদের আগে থেকেই চাকরি ছিলো, তাদেরকেও বাদ দেয়া হলো।
এই চরম দুঃসময়ে লাখ লাখ মুসলমান বেকারত্বের অভিশাপ নিয়ে যাত্রা করলো গ্রামের দিকে। উদ্দেশ্য ছিলো, কৃষিকে আঁকড়ে ধরে কোনো রকমে বেঁচে থাকা।
গ্রামের অবস্থা ছিলো আরো ভয়াবহ।
শাসন ক্ষমতা হস্তগত করার সাথে সাথে ইংরেজ বণিকরা বাংলার প্রাচীন গ্রামের ভিত্তি ভূমিকে ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছিলো। ভেঙ্গে দিয়েছিলো তারা গ্রামের সমাজ কাঠামোকেও। এ কাজে তারা প্রধানত দু’টি অস্ত্র ব্যবহার করলো- ভূমি রাজস্বের নতুন ব্যস্থা ও ভূমি রাজস্ব হিসেবে ফসল বা দ্রব্যের পরিবর্তে মুদ্রার প্রচলন।
এই দুই অস্ত্রের প্রচণ্ড শক্তির আঘাতে স্বল্পকালের মধ্যে প্রাচীন গ্রাম-বাংলার ভিত্তি একেবারে ধূলিসাৎ হয়ে গেলো। শ্মসানে পরিণত হলো হাজার হাজার গ্রাম।
বহুমুখী শোষণ-উৎপীড়নের চাপে পড়ে বাংলার অসহায় কৃষক সমাজ নিঃস্ব হয়ে অনিবার্য ধ্বংসের মুখে এসে দাঁড়ালো।
বাংলার দরিদ্র কৃষক মানেই মুসলমান। আর জমিদার এবং বিত্তবান মানেই হিন্দু।
ক্ষমতা হারিয়ে, চাকরি খুইয়ে মুসলমানরা যখন দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে হতাশাগ্রস্ত, তখন ইংরেজ সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় সর্বস্তরে ক্ষমতা সম্পদের অধিকারী হলো হিন্দু দেওয়ান, গোমস্তা, বেনিয়ান, মুৎসুদ্দিরা। সকল ক্ষেত্রে তখন হিন্দুদেরই একচ্ছত্র দাপট।
কর্নওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বদৌলতে জমির মালিকরূপে পরিগণিত হলো হিন্দুরাই। শুধামাত্র অর্থগুণে দেব, মিত্র, সিংহ, মল্লিক, শীল এমন কি তিলি আর সাহা-রাও রাতারাতি জমিদাররূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করলো।
পুরনো জমিদারদের অনেকেই নানা কারণে জমিদারী বিক্রি করেছিলো। সেই জমিদারী কিনে নিয়েছিলো সম্পদশালী হিন্দু ব্যবসায়ীরা।
নব্য জমিদারদের খাজনা ও বহুবিধ করের চাপের এবং জমিদারদের নিয়োগকৃত নায়েব গোমস্তাদের রোষেপড়ে গরীব চাষীরা হলো এবার ভিটেছাড়া।
একদিকে জমিদার মহাজনের শোষণ-পোড়ণ আর আধুনিক অত্যাচার, অপরদিকে কুশিখ্ষা, অশিক্ষার অভিশাপ। তার ওপর আছে রোগ, মহামারী ও দুর্ভিক্ষ। এ সবকিছু মিলিয়ে মুসলিম চাষীরা এমন এক করুণ ও ভয়াবহ অবস্থার শিকার হলো- যার পরিণতি ছিলো অনিবার্য ধ্বংস।
সরকারী চাকরি পাওয়ার সকল দরোজা বন্ধ হয়ে গেলো মুসলমানদের জন্যে। তাদের মধ্যে যারা ইংরেজী শিখে যোগ্যতা অর্জনের চেষ্টা করলো- তারাও চাকরি পেলো না। কেননা চাকরির বিজ্ঞাপনে তখন স্পষ্ট উল্লেখ থাকতো কেবল হিন্দু প্রার্থদেরই আবেদন গ্রহণযোগ্য।
‘দূরবীন’ নামক কলকাতার একটি ফরাসী পত্রিকা ছিলো।
আঠারো শো ঊনসত্তর সালের জুলাই মাসে চাকরির ক্ষেত্রে মুসলমানদের দুর্দশার কথা বর্ণনা করতে গিয়ে ‘দুরবীন’ পত্রিকাটি লিখেছিলো:
“উচ্চস্তরের বা নিম্নস্তরের সমস্ত চাকরি ক্রমান্বয়ে মুসলমানদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে, বিশেষ করে হিন্দুদের মধ্যে বিতরণ করা হচ্ছে। সরকার সকল শ্রেণীর কর্মচারীকে সমান দৃষ্টিতে দেখতে বাধ্য, তথাপি এমন সময় এসেছে যখন মুসলমানদের নাম আর সরকারী চাকুরিয়াদের তালিকায় প্রকাশিত হচ্ছে না, কেবল তারাই চাকরির জায়গায় অপাংক্তেয় সাব্যস্ত হয়েছে। সম্প্রতি সুন্দরবন কমিশনার অফিসে কতিপয় চারিতে লোক নিয়োগের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়, কিন্তু অফিসাপরটি সরকারী গেজেটে কর্মখালির যে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেন তাতে বলা হয় যে, “শূণ্য পদগুলিতে কেবলমাত্র হিন্দুদের নিয়োগ করা হবে।”
তখনকার দিনে অফিস আদালত ও পুলিশ বিভাগেও কেবলমাত্র হিন্দুদেরকে নিয়োগ করার নির্দেশ দেয়া হতো।
শুধা চাকরি নয়। শিক্ষা ও ব্যবসার ক্ষেত্রেও মুসলমানদের অবস্থা ছিলো দুর্ভাগ্যজনকভাবে সংকটময়।
অপরদিকে ধর্মীয়ভাবেও মুসলমানরা ছিলো অনগ্রসর। ইসলাম থেকে, ইসলামের মূল শিক্ষা ও আদর্শ থেকে তারা অনেক অনেক দূরে সরে গিয়েছিলো।
হিন্দুদের পাশাপাশি দীর্ঘকাল বসবাস করার কারণে এবং অসচেতন থাকার ফলে তারা শিরক ও বিদআতের মতো বড়ো বড়ো গুনাহের কাজে লিপ্ত থাকতো। হিন্দুয়ানী অপসংস্কৃতির জোয়ারে ভেসে গিয়েছিলো তখনকার অধিকাংশ মুসলিম পরিবার।
ঠিক এমনি এক ক্রান্তিকালে, এমনি এক অস্থির দুঃসময়ে জন্মলাভ করলেন এই উপমহাদেশের সংগ্রামী নেতা- হাজী শরয়তুল্লাহ।
জন্ম ও শৈশব
সতেরো শো একাশি সাল।
দিনিটির কথা কেউ আর বলতে পারে না।
এই বছরের কোনো একদিনে হাজী শরীয়তুল্লাহ জন্মলাভ করেন। গ্রামের নাম শামাইল।
গ্রাটি ছিলো বর্তমান মাদারীপুর জিলার বাহাদুরপুরের অন্তর্গত।
তাঁর জন্ম হয়েছিলো একটি প্রখ্যাত জমিদার পরিবারে।
শরীয়তুল্লাহর আব্বার নাম আবদুল জলিল তালুকদার।
তিনি ছিলেন একজন বিখ্যাত ব্যক্তি।
তা৭র নাম ডাক ছিলো চারদিকে।
তিনি ছিলেন যেমনি ভদ্র, তেমনি দয়ালূ। এ কারণে সবাই তাঁকে ভালোবাসতো প্রাণ দিয়ে।
শরীয়তুল্লাহর পিতা আবদুল জলিল ছিলেন একজন প্রজাবৎসল তালূকদার। অন্যান্য তালুকদারের মতো তিনি সাধারণ প্রজাদের ওপর জুলুম-নির্যাতন চালাতেন না।
শোষণের কুড়াল মারতেন না প্রজাদের মাথায়।
তিনি ছিলেন তাদের প্রতি অত্যন্ত দয়ালূ।
সাধারণ প্রজাদের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নার সাথে আবদুল জলিল নিজেকেও যুক্ত করতেন। শরীক হতেন তাদের ব্যাথা-বেদানার সাথে
সমবেদনা জানাতেন। সাহায্য করতেন সাধ্য মতো। এজন্যে তাঁর নামটি ছড়িয়ে পড়েছিলো অনেক দূর পর্যন্ত।
সবাই তাঁকে শ্রদ্ধা করতো। সম্মান দেখাতো।
শরীয়তুল্লাহ এই বিখ্যাত ও সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।
আবদুল জলিল তালুকদার চেয়েছিলেন- তাঁর ছেলেও হবে মানুষের মতো মানুষ।
সে হবে শিক্ষিত এবং আদর্শবান।
সাধারণ মানুষের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করবে সে।
শরীয়তুল্লাহ শৈশবে বর্ণজ্ঞান লাভ করে তাঁর পরিবারের কাছে। তারপর গ্রারেম মক্তবে।
পিতার ইচ্ছা ছিলো শরীয়তুল্লাহর শিক্ষা জীবনের সফলতা নিজের চোখে দেখে যাবেন।
কিন্তু তিনি সে সময় আর পাননি।
শরীয়তুল্লাহ এবং এক কন্যা সন্তানকে শিশু অব্থায় রেখে ইন্তেকাল করলেন আবদুল জলিল তালুকদার।
আবদুল জলিল তালুকদারের ছিলেন আরও দুই ভাই।
এক ভাইয়ের নাম মুহাম্মদ আজিম। তিনি শামাইল গ্রামেই থাকতেন।
অপর ভাই মুহাম্মদ আশেক। থাকতেন মুর্শিদাবাদ। তিনি মুর্শিদাবাদের নবাবের দরবারে মুফতি ছিলেন।
তিনি ছিলেন মস্ত বড়ো এক আলেম।
পিতার ইন্তিকালের পর বালক শরীয়তুল্লাহর লালন-পালন এবং শিক্ষার দায়িত্বগ্রহণ করলেন আপন চাচা মুহাম্মদ আজিম। তিনি ছিলেন নিঃসন্তান। মুহাম্মদ আজি আপন সন্তানের মতোই আদর যত্নে লালন করছিলেন শরীয়তুল্লাহকে।
অসীম স্নেহ আর ভালোবাসায় তিনি ভরে দিতেন শরীয়তুল্লাহর শিশুমনকে। কিন্তু শরীয়তুল্লাহর শিক্ষার ব্যাপারটি ছিলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ
তখন গ্রামে ছিলো না ভালো কোনো স্কুল, মাদরাসা। ছিলো না তেমন কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। সুতরাং শিক্ষা লাভের জন্যে অবশ্যই দূরে কোথাও যেতে হবে।
কিন্তু কোথায় যাওয়া যায়?
একান্তে ভাবেন কিশোর শরীয়তুল্লাহ!
কলকাতায় গমন
শিক্ষার প্রতি ছিলো বলক শরীয়তুল্লাহর অদম্য আগ্রহ।
এই আগ্রহের কারণে অল্প বয়সেই শরীয়তুল্লাহ পাড়ি জমালেন শামাইল থেকে সুদূর কলকাতা।
তাঁর এই সিদ্ধান্তে চাচা আজিমও খুব খুশি হলেন। কারণ তিনিও চান মানুষের মতো মানুষ হোক আদরের শরীয়তুল্লাহ।
সালীট ছিলো সতেরো শো তিরানব্বই।
কলকাতায় গিয়ে শরীয়তুল্লাহ ওঠেন মাওলানা বশারত আলীর কাছে।
মাওলানা বশারত আলী ছিলেন এক মস্ত বড়ো আলেম। ছিলেন পাক্কা দীনদার।
বালক শরীয়তুল্লাহর শিক্ষার প্রতি অসম্ভব আগ্রহ দেখে তিনি খুব খুশি হলেন। অত্যন্ত আন্তরিকতা ও স্নেহের সাথে তিনি শরীয়তুল্লাহর সামনে তুলে ধরলেন শিক্ষা ও জ্ঞানের প্রদীপ।
শরীয়তুল্লাহও ছিলেন অত্যন্ত শান্ত ও মেধাবী। ভদ্রতা ছিলো তাঁর সকল সময়ের ভূষণ।
একাগ্রতার সাথে তিনি মাওলানা বশারত আলীর কাছে পড়তে থাকলেন। শরীয়তুল্লাহর লেখাপড়ার প্রতি মনোযোগ দেখে এবং তাঁর চরিত্র-মাধুর্যে মোহিত হয়ে মাওলানা বশারত আলী তাঁর এই প্রিয় ছাত্রের লেখা-পড়ার যাবতীয় দায়িত্বভার তুলে নিলেন নিজের কাঁধে।
শরীয়তুল্লাহকে তিনি পরবর্তীতে ভর্তি করে দিলেন হুদলী মাদরাসায়। মাদরাসাটি ছিলো হুগলিরি ফুরফুরায়।
মাদরাসায় ভর্তি হবার পর শরীয়তুল্লাহ লেখা-পড়ায় আরও বেশী মনোযোগী হলেন।
দুর্ঘটনার কবলে
কলকাতায় মাওলানা বশরাত আলীর তত্ত্বাবধানে লেখা-পড়া করার সময় শরীয়তুল্লাহ একবার মুর্শিদাবাদ গেলেন।
সেখানে থাকেন চাচা মুফতী মুহাম্মদ আশিক।
চাচার সাথে সাক্ষাৎ করলেন শরীয়তুল্লাহ। এরপর থেকে তিনি প্রায়ই যেতেন চাচার কাছে। হৃদয়ের টানে।
চাচা ছিলেন অত্যন্ত কর্মব্যস্ত মানুষ।
এজন্য বহুদিন হলো আপন মাতৃভূমিতে আসার সুযোগ পাননি তিনি।
এর মধ্যে শরীয়তুল্লাহর ওপর দিয়েও গড়িয়ে গেছে অনেকটা সময়। তিনিও অনেকদিন যাবত বাড়ি ছাড়া।
যোগাযোগ নেই গ্রামের সাথে। গ্রামের মানুষ আর অবারিত সবুজের সাথে।
গ্রামে ফেরার জন্যে তাই মনটা তাঁর কেবলই আনচার করে ওঠে।
ব্যাকুল হয়ে ওঠে তাঁর কিশোর হৃদয়।
চাচা মুফতী আশক একদিন শরীয়তুল্লাহকে বললেন, চলো আমরা বাড়ি থেকে একবার বেড়িয়ে আসি।
কথাটি শুনার সাথে সাথে শরীয়তুল্লাহর চোখে আপন বাস্তু ভিচার ছবিটা ছবির মতো ভেসে উঠলো।
তাঁর হৃদয়টা দুলে উঠলো মুহূর্তেই।
তিনি রাজি হয়ে গেলেন চাচার কথায়।
মুর্শিদাবাদ থেকে রওয়ান হলেন তাঁরা। নৌকাযোগে আসছেন নিজ গ্রাম- ফরিদপুরেরর শামাইলে।
সাথে আছে চাচা ও চাচী। নৌকা চলছে গঙ্গার বুক দিয়ে। পানি কেটে কেটে।
শাঁ শাঁ গতিতে। প্রমত্তা গঙ্গ!
ভয়ঙ্কর তার স্রোত!
তার ওপর আকাশে মেঘ এবং ঝড়ের পূর্বাভাস। ওলোট পালোট বাতাস। ঝড়ের ইঙ্গিত! তবুও নৌকা চলছে প্রবল গতিতে।
হঠাৎ শুরু হয়ে গেলো গঙ্গার বুকে ঝড়েড় দপাদপি! সে কি ঝড়!
ঝড়ের কবলে পড়ে মুহূর্তেতই যাত্রী বোঝাই নৌকাটি তলিয়ে গেলো গঙ্গার বুকে! আর তারই সাথে গঙ্গার প্রচণ।ড স্রোতের তোড়ে চিরতরে হারিয়ে গেলেন চাচীজান। হারিয়ে গেলেও চাচাও।
হারিয়ে গেলেন একজন বিখ্যা আলেমে দীন- মুফতী আশিক।
গঙ্গা তখনো ফুঁসছে ক্রমাগত।
গঙ্গার সেই ভয়ালো ঝড় আর ঢেউকে উপেক্ষা করে আল্লাহর অসীম রহমতে সাঁতরিয়ে কূলে উঠে দাঁড়ালেন শরীয়তুল্লাহ!
অলৌকিক ব্যাপার বটে! প্রাণে বেঁচে গেলেণ তিনি।
মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে গিয়ে অশেষ শুকরিয়া জানালেন মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে।
কূরে উঠে তিনি গঙ্গার দিকে তাকিয়ে হতাশ হলেন। কেঁপে উঠলো তাঁর বুক!
শূন্যতায় ভরে গেলো তাঁর কোমল হৃদয়।
কূরে দাঁড়িয়ে তিনি গঙ্গার বুকে কোথাও খুঁজে পেলেন না চাচা, চাচী এবং সেই নৌকাটিকে!
ফরিদপুর আর আসা হলেঅ না শরীয়তুল্লাহর
দেখা হলো না আর প্রাণ-প্রিয় মাতৃভূমি শামাইল।
এক বুক বেদনা আর স্বজন হারানো কষ্ট নিয়ে তিনি আবারো ফিরে গেলেন কলকাতায়।
ফিরে গেলেন প্রিয় শিক্ষক মাওলানা বশারত আলীর কাছে।
কলকাতায় ফেরার পর শরীয়তুল্লাহর মুখ থেকে সকল কথা শুনলেন মাওলানা বশারত আলী।
শুনলেন তাঁর স্বজন হারানোর বেদনার কথা। নৌকাডুবির কথা।
তিনি শুনলেণ শরীয়তুল্লাহর আল্লাহর রহমতে অলৌকিকভাবে বেঁচে যাবার কথা।
সকল কথা শুনার পর মাওলানা বশারত আলী অবাক হলেন।
তিনি শরীয়তুল্লাহকে আরো বেশি আদর-স্নেহে কাছে টেনে নিলেন।
সতেরো শো নিরানব্বই সাল।
মাওলানা বশারত আলী মক্কায় যাবার সিদ্ধান্ত নিলেন।
মক্কায় যাবেন তিনি নবীজীর (সা) পবিত্র কবর মুবারক যিয়ারত করার জন্যে। শরীয়তুল্লাহকে সাথে নেবার ইচ্ছাও প্রকাশ করলেন তিনি।
কি সৌভাগ্য তাঁর!
এক অলৌকিকভাবে তাঁর মক্কা যাবার স্বপ্ন বাস্তবায়ন হতে যাচ্ছে!
তিনি ভাবতেই পারেননি এতো সহজে মক্কায় যেতে পারবেন।
আল্লহর কুদরত ও রহমতের শুকরিয়া জানিয়ে তিনি রাজি হয়ে গেলেন। রাজি হয়ে গেলেন মাওলানা বশারত আলীর প্রস্তাবে।
কিছু দিনের মধ্যেই শরীয়তুল্লাহ তাঁর প্রিয় শিক্ষক মাওলানা বশারত আলীর সাথে মক্কার পথে যাত্রা শুরু করলেন।
মক্কা জীবনে
মাওলানা বশারত আলীর সাথে মক্কায় আসার পর হাজী শরীয়তুল্লাহর বুকটা আনন্দে ভরে উঠলো।
তাঁর ছিলো শিক্ষার প্রতি অসম্ভব আগ্রহ।
তিনি মক্কাতেও শিক্ষালাভের জন্য অপ্রাণ চেষ্টা করলেন। শরীয়তুল্লাহ মক্কায় ছিলেণ একটা বিশ বছরের মতো।
অনেক দীর্ঘ সময়।
এই দীর্ঘ সময়ে তিনি মক্কার বহু বিখ্যাত শিক্ষকের কাছে পড়াশুনা করলেন। কিতাবী শিক্ষার পাশাপাশি তিনি ইসলামের ব্যবহারিতক দিক সম্পর্কেও সম্যক জ্ঞান লাভ করলেন।
যেহেতু মক্কায় গেছেন। সেই কারণে হজ পালন করাটা তো আর হাত ছাড়া করা যায় না!
শরীয়তুল্লাহ সাথে সাথে হজ পালনের পর্বটা সেরে নিলেন।
কি আশ্চর্যের বিষয়!
আপন সাধনা ও শ্রমের বলে হাজী শরীয়তুল্লাহ একজন উচ্চ শিক্ষিত আলেম হিসাবে সুদূর মক্কাতেও বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছিলেন।
বাংলাদেশথেকে মক্কা অনেক- অনেক দূরের পথ।
একটি ভিন্ন দেশ। ভিন্ন তাদের ভাষায়। ভিন্ন তাদের শিক্ষা ব্যবস্থাও শিক্ষাদান পদ্ধতি।
কিন্তু তা হলে কি হবে?
হাজী শরীয়তুল্লাহর খ্যাতি তখন মক্কার চারদিকে।
সেই খ্যাতির সৌরভে মৌ মৌ করছে মক্কার বিস্তৃত প্রান্তর।
ইসলাম সম্পর্কে তাঁর পাণ্ডিত্যের কথা তখন সবার মুখে মুখে।
তাঁর জ্ঞানের বহরের কথা মক্কার শিক্ষিত মানুষ মাত্রই জেনে গেছেন।
অবাক হবারই তো কথা!
তাঁর পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে সেখানকার মানুষ হাজী শরীয়তুল্লাহকে শিক্ষক নিযুক্ত করলেন।
হাজী শরীয়তুল্লাহ মক্কায় বিশ বছর অবস্থান করার সময়ে বেছে নেন শিক্ষকতার এই মহান পেশা।
তিনি মক্কার নামী-দামী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা করতে থাকেন।
এতে করে তাঁর সময়টা ভালোই কাটছিলো। আরো বৃদ্ধি পাচ্ছিলো তাঁর জ্ঞানের বহর।
এই সময়ে তিনি সন্ধান পেলেন মক্কার আর এক বুজুর্গ ব্যক্তি। তাঁর নাম মাওলানা তাহের চোম্বল।
মক্কায় তিনি ছোটো আবু হানিফা নামে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।
হাজী শরীয়তুল্লাহ এই বুজুর্গ আলেমে দীন- মাওলানা তাহের চোম্বলের কাছে প্রায়ই যেতেন।
মাওলানা তাহের মক্কায় একজন আধ্যাত্মিক পণ্ডিত ও সংস্কারক হিসাবেও পরিচিত ছিলেন।
তাঁর চরিত্র মাধর্যে এবং তা৭র শিক্ষা ও সংস্কারে মুগ্ধ হয়ে হাজী শরীয়তুল্লাহও তাঁকে অনুসরণ করেন।
মক্কায় বিশ বছর ছিলেন হাজী শরীয়তুল্লাহ। এ সময়ের মধ্যে তিনি একাধিক হজ পালন করেন।
স্বদেশের দিকে
মক্কা বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা দান এবং মাওলানা তাহের চোম্বলের কাছে ইসলাম ও আত্মশুদ্ধি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে থাকেন হাজী শরীয়তুল্লাহ।
কিন্তু স্বদেশে ফেরার জন্যে তাঁর হৃদয়টা ব্যাকুলতা হয়ে উঠলো।
কেবলই মনে পড়তে থাকলো তাঁর আপন মাতৃভূমির কথা। স্বজনদের কথা। প্রিয় চাচার কথা।
চাচা মুহাম্মদ আজিমের অসুস্থতার খবরও তিনি পেয়ে গেছেন।
এসব কথা ভাবতে গিয়ে মক্কার প্রবাস জীবনে অস্থির হয়ে ওঠেন হাজী শরীয়তুল্লাহ।
সিদ্ধান্ত নেন মক্কা থেকে স্বদেশে ফিরে আসার।
অবশেষে তিনি ফিরে এলেন স্বদেশের মাটিতে। সময়টা ছিলো আঠারো শো আঠারো সাল।
হাজী শরীয়তুল্লাহ দীর্ঘ প্রবাস জীবন শেষে যখন নিজ গ্রাম শামাইলে পৌছুলেন,তখন দেখলেন তাঁর একমাত্র জীবিত চাচা মুহাম্মদ আজিম তালুকদার ভীষণ অসুস্থ।
প্রাণ-প্রিয় চাচার এই করুণ অবস্থা দেখে ডুকরে কেঁদে উঠলেন হাজী শরীয়তুল্লাহ!
চারদিকে আঁধার কালো
খুব শৈশবে গ্রাম ছেড়েছিলেন শরীয়তুল্লাহ।
তিনি মক্কা থেকে ফিরে এসে তখনকার সেই পরিচিত মুখগুলোর মধ্যে অনেককেই আর দেখতে পেলেন না!
এর মধ্যে হারিয়ে গেছে তাঁর কত যে চেনা মুখ! কত যে কাছে মানুষ! কত যে খেলার সাথী!
স্বজন হারানোর এই বেদনা হাজী শরীয়তুল্লাহকে খুব ব্যথিত করে তুললো। কিন্তু তার চেয়েও তিনি বেশি ব্যথিত হলেন চার পাশের মানুষ ও তাদের পরিবেশ দেখে।
আতকে উঠলেন তাদের অধঃপতন দেখে!
কুসংস্কার, অশিক্ষা, কুশিক্ষা, অভাব দারিদ্র আর শোষণ নির্যাতনে মুষড়ে পড়া মুসলিম পরিবারগুলোর দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারেন না
হাজী শরীয়তুল্লাহ!
চারদিকে আঁধারের কালো ছায়া!
এদেশে তখনো ইংরেজদের দখলে।
ইংরেজদের শোষণ আর অত্যাচারে অতিষ্ট শহরের মানুষ। তার চেয়েও বেশি অতিষ্ট গ্রামের মানুষ।
পাড়া-গ্রামে চলছে অত্যাচারী জমিদার, মহাজন আর নীল করদের একচেটিয়া দাপট।
শুধু ইংরেজই নয়।
এদেশের হিন্দু জমিদাররাও তাদের সাথে মিশে অত্যাচারের বিষে জর্জরিত করছে সাধারণ মুসলমানকে।
সে সময়ে গ্রামের অধিকাংশ মুসলমানই ছিলো অত্যন্ত দরিদ্র।
তাদেরকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে দিতো না একদিকে ইংরেজ, নীলকর এবং অপরদিকে এ দেশীয় হিন্দু এবং হিন্দু মহাজন ও জমিদাররা। অসহায় দরিদ্র মুসলমানদের অধিকাংশই ছিলো অশিক্ষিত।
একটু যারা শিক্ষিত তারাও ছিলো অনেকটা অসচেতন। ইংরেজরা হিন্দু ও হিন্দু জমিদারকে খুব সুনজরে দেখতো। হিন্দুদেরকে তারা খুব কদর করতো। আর মুসলমানরা ছিলেঅ তাদের দু’চোখের বিষ।
তারা মুসলমানদেরকে শত্রু ভাবতো।
তাই তারা সুকৌশলে সকল সময় হিন্দুদেরকে ক্ষেপিয়ে তুলতো দরিদ্র অশিক্ষিত মুসলমানদের ওপর।
ইংরেজদের আশকারা আর মদদ পেয়ে হিন্দুরা ছলে-বলে-কৌশলে মুসলমানদের গ্রাস করতে উদ্যত হতো।
তারা গ্রাস করতো মুসলমানদের অর্থ-সম্পদ, জমি-জায়গা।
তাতেও তারা খুশি হতো না।
এরপর তারা মুসলমানদের ধর্মীয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক দিক দিয়েও ধ্বংস করার চেষ্টা করতো সর্বক্ষণ।
মুসলমানদের ইসলাম থেকে, তাদের ঐতিহ্য থেকে দূরে রাখার সকল প্রকার অপকৌশল প্রয়োগ করতো হিন্দুরা।
তাদের হাতে ক্ষমতা আর অর্থ থাকার কারণে তারা সহজেই প্রভাবিত করতে পারতো দরিদ্র-অশিক্ষিত মুসলমানদেরকে।
এইভাবে এক সময় মুসলমানরা কুসংস্কারের অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে পড়লো। হাজী শরীয়তুল্লাহ দেখলেন মুসলমানদের এই করুণ পারিবারিক ও সামাজিক অবস্থা।
তিনি দেখলেন, মুসলমানরা রোযা-নামাযসহ আল্লাহর ইবাদাত ছেড়ে দিয়ে, আপন সংস্কৃতি ভুলে গিয়ে হিন্দুদের সংস্কৃতিকে গ্রহণ করে নিয়েছে!
তারা নামেই কেবল মুসলমান আছে।
তাদের মধ্যে নেই ইসলামের কোনো ছায়া চিহ্ন।
ইসলামের কোনো কিছুই তারা পালন করে না।
দীর্ঘকাল হিন্দুদের দ্বারা প্রভাবিত হবার কারণে হিন্দুয়ানী আচার অনুষ্ঠান ও হিন্দু সংস্কৃতিতে তারা গা ভাসিয়ে দিয়েছে।
ইসলারেম যে মৌলিক ও পৃথক সংস্কৃতি বলে কিছু আছে- এ কথাও তারা ভুলে গেছে।
কি সর্বনাশে ব্যাপার!
তাদের এই অধঃপতন দেখে খুবই মর্মামহত হলেন হাজী শরীয়তুল্লাহ।
তিনি পথভোলা মানুষের কাছে নতুন করে ইসলামের দাওয়াত দেবার প্রয়োজনবোধ করলেন। এই বোধ থেকেই তিনি শুরু করলেন ইসলামের দাওয়াতী তৎপরতা।
বেদগান করলেন তাঁর সংস্কার আন্দোলন।
মানুষকে আহ্বান জানান তিনি সত্যের দিকে। আল্লাহর দিকে।
সাধারণ মুসলমানকে তিনি বুঝান ইসলারেম আকীদা-বিশ্বাস।
বুঝান ইসলামের সুমহান আদর্শ ঐতিহ্য।
বুঝান সত্য আর মিথ্যার পার্থক্য।
কিন্তু কি আফসোস!
গ্রামের মুসলমানরা এতোটাই অন্ধকারে ডুবেছিলো যে, হাজী শরীয়তুল্লাহর শত আহ্বানেও তারা প্রথমত এতোটুকু সাড়া দেয়নি।
তারা চিনতে ভুল করলো সত্য-সঠিক পথ। বুঝতে ভুল করলো হাজী শরীয়তুল্লাহকে।
অন্ধ মানুষের মধ্যে দীনের দাওয়াত দিতে গিয়ে প্রথম দিকেই ব্যর্থ হলেন হাজী শরীয়তুল্লাহ।
তাদের গুমরাহীতে ভীষণ কষ্ট পেলেন তিনি।
ভেবেছিলেন, অন্ধকারাচ্ছন্ন-পথভোলা গ্রামের আপন মানুষকে তিনি পথের দিশা দেখাবেন।
তাদেরকে আবার ইসলামের আলোয় আলোকিত করবেন। কিন্তু পারলেন না তিনি।
পারলেন না হাজী শরীয়তুল্লাহ।
কারণ তাঁর কথা কেউ শুনলো না।
আবারো মক্কার পথে
আপন গ্রামের মানুষকে সত্যের পথে ডেকে যখন তাদের কোনো সাড়া পেলেন না, তখন কিছুটা হতাশ হয়ে আবারো মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করলেন হাজী শরীয়তুল্লাহ।
বুকে তাঁর ব্যর্থতার যন্ত্রণা! কষ্টের তুফান! কোনো যানবাহনে নয়।
এবার চললেন তিনি সম্পূর্ণ পায়ে হেঁটে।
মক্কায় যাবার পথে প্রথমে তিনি বাগদাদে গেলেন।
বাগদাদে ঘুমিয়ে আছেন বহু শহীদ, গাজী, পীর-দরবেশ, আলেম-উলামা এবং অজস্র নেক ব্যীক্ত।
হাজী শরীয়তুল্লাহ সেই সকল পবিত্র কবর যিয়ারত করেন। যিয়ারত করেন যারা দীনের জন্যে, ইসলামের জন্যে নিজেদের জীবনকে কুরবানী করে ঘুমিয়ে পড়েছেন গহীন কবরে।
এই সকল কবরের মধ্যে আছে দয়ার নবীজীর (সা) কলিজার টুকরা, নয়নের মণি নাতি- হযরত হুসাইনের (রা) পবিত্র কবরও।
দীনের জন্যে আত্মত্যাগের এক বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী ইমাম হোসাইনের (রা) স্মৃতি-বিজড়িত কারবালা প্রান্তরে ইমামের শাহাদাতগাহ, তাঁর কবর এবং আবদুল কাজের জিলানীর (র) কবরও যিয়ারত করেন হাজী শরীয়তুল্লাহ।
তিনি ঘুরে ঘুরে বিখ্যাত সকল ব্যীক্তর কবর যিয়ারত করলেন।
এরপর তিনি বাইতুল মাকদিস ও মিসর সফর শেষে পৌঁছে যান পবিত্র মক্কায়। মক্কায় পৌঁছে হাজী শরীয়তুল্লাহ পুনরায় খোঁজ করেন তাঁর প্রিয় শিক্ষক মাওলানা তাহের আলীকে।
তাঁর সাথে সাক্ষাতের পর হাজী শরীয়তুল্লাহ আবারো হজ পালন করেন। তারপর রওয়ানা হলেন মদীনার পথে।
হাজী শরীয়তুল্লাহ এবার মাত্র দু’বছর থাকেন মক্কায়ে।
সেখানে থাকাকালীন সময়ে তিনি গভীরভাবে ইসলামের খুঁটিনাটি বিষয়সমূহ ছাড়াও আধ্যাত্মিক সাধনায় নিজেকে ব্যস্ত রাখেন।
তিনি মদীনায় গিয়ে নবীজীর (স) কবর মুবারক যিয়ারত করেন।
রাসূলের (সা) পবিত্র রওজযা মুবারকে দাঁড়িয়ে হাজী শরীয়তুল্লাহ স্বদেশের মুসলমানদের বিপর্যয়ের কথা স্মরণ করে তাদের মুক্তি ও হিদায়েতের জন্যে বিশেষভাবে দোয়াও করলেন।
সেখানে অবস্থানকালে তিনি একে একে তিনবার প্রাণ-প্রিয় রাসূলুল্লাহকে (সা) স্বপ্নে দেখেন।
রাসুল (সা) প্রতিবারেই তাঁকে দেশে ফিরে ইসলাম প্রচারের নির্দেশদেন। এই আশ্চর্যজনক স্বপ্নের কথা হাজী শরীয়তুল্লাহ খুলে বললেণ তাঁর মক্কার শিক্ষক মওলানা তাহের আলীকে।
বিজ্ঞ আলেমে দ্বীন মাওলানা তাহের আলী সকল কথা শুনে হাজী শরীয়তুল্লাহকে একজন সৌভাগ্যবান ব্যক্তি বলে অভিহিত করলেন।
তারপর তাঁকে বললেণ, স্বদেশে ফিরে ইসলাম প্রচারের কাজে আত্মনিয়োগ করতে।
দু’বছর মক্কা ও মদীনা সফর করার পর হাজী শরীয়তুল্লাহ আবারো রওয়ানা দিলেন স্বদেশের পথে।
সালটি ছিলো আঠারো শো বিশ।
আল্লাহর কি অপার মহিমা!
হাজী শরীয়তুল্লাহ এবার দেশে ফিরে দেখেন অন্য অবস্থা!
ভিন্ন এক পরিবেশ!
তিনি দেখেন চারদিকে জেগে উঠেছে মজলুম জনতা।
আন্দোলন এবং সংগ্রামের ঝড় উঠেছে হিন্দু জমিদার এবং ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে।
এসব দেখে তিনি অত্যন্ত খুশী হলেন। আর তাঁর দোয়া কবুল হবার জন্য শুকরিয়া জানালেন মহান রাব্বুল আলামীনকে।
হাজী শরীয়তুল্লাহর বুকে আরও প্রচণ্ড বেগে শুরু হলো সেই ঝড়ের তোলপাড়!
বারবার লড়ে যায় বীর
বারো শো তিন সাল থেকে সাড়ে পাঁচশো বছর পর্যন্ত বছর পর্যন্ত মুসলমানরা বাংলার শাসন পরিচালনা করেছিলেন।
অবশেষে এলো সতেরো সাতান্ন সাল।
পলাশীর যুদ্ধে পরাজিত হলেন বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদ্দৌলাহ। এই যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে ইংরেজরা কেড়ে নিলো মুসলমানের হাত থেকে বাংলাদেশের শাসন ক্ষমতা।
কেড়ে নিলো তারা জনগণের সকল স্বাধীনতা।
ইংরেজ শাসনের সময় হিন্দুরা ছিলো তাদের অনুগত দাসানুদাস।
আর মুসলমানা ছিলো বিদ্রোহী।
পলাশীর যুদ্ধে পরাজয় বরণ করে মুসলমানরা কেবল রাজ্যই হারালেনা, তারা হারালো সর্বস্ব।
একদিন যে মুসলমানের হাঁক-ডাকে সরব হয়ে উঠতো চারদিক, মুহূর্তেই থেমে গেলা তাদের সেই তুমুল গর্জন।
একদিন যে মুসলমানের জন্যে দরিদ্র কিংবা নিঃস্ব হওয়া চিলো প্রায় অসম্ভব, ইংরেজরা ক্ষমতা দখলের পরপরই সেই মুসলমানরা পরিণত হলো কাঠুরিয়া এবং ভিস্তিওয়ালায়।
লাঞ্চিত এবং বঞ্চি হতে থাকলো তারা নির্মমভাবে।
মীর জাফরের মতো গুটিকয়েক অপরিণামদর্শী। উচ্চাভিলাষী নামদারী মুসলমান ইংরেজ ও হিন্দুদের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে বেপথু হয়ে সিরাজদ্দৌলাহকে পলাশীতে বিপর্যয়ের মধ্যে ফেলে দিলো।
সেকান থেকেই মুসলমানের ভাগ্যে অংকিত হয়ে গেলো অপমমান আর লাঞ্ছনার কালো চিহ্ন।
তবুও সংগ্রাম থেমে থাকেনি একটি মুহূর্তের জন্যেও। কেনই বা থামবে?
মুসলমানদের রক্তে মিছে আছে ঈমান আর অসীম সাহসের বারুদ! প্রয়োজনে তারা জ্বলে ওঠে বারবার। গর্জে ওঠে সিংহরে মতো। যেমন গর্জে উঠেছিলো সেদিন অনেকেই। ইংরেজদের দুঃশাসন আর হিন্দুদের অত্যাচার থেকে এই দেশকে মুক্ত করার জন্যে, এই জাতিকে রক্ষা করার জন্যে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো সময়ের সাহসী পুরুষেরা।
আবারো জেগে উঠলো তাদের সাথে মুসলমান।
তাদের সংগ্রামকে প্রতিহত করার জন্যে হিন্দুদের সহযোগিতায় ইংরেজরাও তৎপর হয়ে উঠলো।
মুসলমানদের ওপর তারা চালাতে শুরু করলো অকথ্য জুলুম আর নির্যাতনের স্টিম রোলার।
তবুও থেমে থাকলো না সংগ্রামের দাবানল!
সতেরো শো চৌষট্টি সাল।
বিদ্রোহী নবাব মীর কাসিম বাংলার স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের জন্যে প্রত্যক্ষ যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।
কিন্তু বক্সারের যুদ্ধে তিনি পরাজিত হলেন চরমভাবে। ব্যর্থ হলো প্রাণ-প্রিয় বাংলঅকে রক্ষা করার তাঁর সর্বশেষ প্রচেষ্টাও।
বক্সারের যুদ্ধের পূর্বেই জেগে উঠেছিলো এদেশের আর এক বিদ্রোহী গোষ্ঠী। ‘ফকির বিদ্রোহ’ নামে খ্যাত এই বিদ্রোহী গোষ্ঠীতে ছিলেন সেই যুগের বহু পীর, ফকির ও অসংখ্য আলেম।
এই বিদ্রোহের নাম ছিল ‘ফকির বিদ্রোহ’।
ফকির বিদ্রোহের নেতা ছিলেন দুঃসাসী এক লড়াকু সৈনিক মজনু শাহ।
সতেরো শো তেষট্টি সাল।
ফকির বিদ্রোহীরা আকস্মিকভাবে আক্রণ করলেন বাকেরগঞ্জ ইংরেজ কোম্পানীর কুঠি।
তাঁরা মীর কাসিমের বাহিনীতেও যোগ দিয়েছিলেন।
তাঁরা সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিলেন ইংরেজদের বিরুদ্ধে। ফকির বিদ্রোহীদের নেতা মজনু শাহরে মৃত্যুর পর মুসা শাহ, চেরাগ আলী, সোবহান শাহ, মাদার বকশ, করিম শাহ প্রমুখ ফকির নেতা এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন।
তাঁদের সংগ্রাম ছিলো মূলত ইংরেজদের বিরুদ্ধে।
এই বিদ্রোহের ফলে ইংরেজ কোম্পানীর সৈন্যদের সাথে তাঁদের অনেক যুদ্ধ হয়েছে।
অনেক সংঘর্ষ হয়েছে।
কিন্তু তারা এতোটুকুও পিছু হটেননি। বরং বাংলাদেশের উত্তর অঞ্চলের একটি বিশাল এলাকা জুড়ে তাঁরা ইংরেজদেরকে কাঁপিয়ে তুলেছিলেন।
তাঁদের সেই সংগ্রামের কথা আজো ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা রয়েছে।
আঠারো শো ছাব্বিশ সাল।
ফকির বিদ্রোহ যখন একটু ঝিমিয়ে পড়েছে তখনই গর্জে উঠলেন আর এক সাহসী সৈনিক- সৈয়দ আহমদ শঞীদ!
তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে, অত্যাচারী শিখ রাজার বিরুদ্ধে এক মহা বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন।
তাঁর আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিলো মুসলমানদের আল কুরআন ও আল হাদীসের শিক্ষায় পূর্ণভাবে ফিরে আনা এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের সময়ের মতো ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা।
মুসলমানদের স্বাধীনতা এবং ইসলামের আদর্শ ও ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠায়ও এই আন্দোলনের বিশেষ ভূমিকা ছিলো।
এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে সৈয়দ আহমদ শহীদ তাঁর আন্দোলনকে বেগবান করে তুলেচিলেন বাঁধভাঙ্গা স্রোতেরমতো।
আফগান সীমান্তের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ঘাঁটি গেড়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে মুসলমানরা শুরু করলো মুক্তির সংগ্রাম।
আঠারো শো ছাব্বশ সালে ইংরেজ-মিত শিখদের সাথে তাদের প্রথম যুদ্ধ হলো।
ভয়ংকর এক যুদ্ধ!
সৈয়দ আহমদ শহীদ এই প্রত্যক্ষ সংগ্রাম শুরুর প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিলেন প্রায় এক দশক আগে।
বাংলাদেশসহ গোটা ভারত সফর করে তিনি সকল মুসলমাকে জাগিয়ে তুলেছিলেন।
আছারো শো একত্রিশ সাল।
এই বিদ্রোহের নায়ক সৈয়দ আহমদ বেরেলভী বালাকোটে শাহাদাত বরণ করলেন।
বিশ্বাসঘাতকদের শিকার হয়ে তিনি এবংতাঁর শীর্ষস্থানীয় সাথীরা শাহাদাত বরণ করেছিলেন।
বালাকোটে যারা শাহাদাত বরণ করেন তাঁদের মধ্যে নয়জন বাংলাদেশীর নাম পাওয়া যায়।
আহতদের মধ্যে ছিলেন আরও চল্লিশ জন।
নারকেল বাড়িয়ার রণাঙ্গনে পরাজয় ও শাহাদাত বরণ করেন বাংলার আরেক সিংহ পুরুষ, দুঃসাহসী- সেনাপতি সাইয়েদ নিসার আলী তিতুমীর!
সেটিও ছিলো আঠারো শো একত্রিশ সাল।
মহা বিস্ময়েরই ব্যাপার বটে!
এই সংগঠন আঠারো শো ছাব্বিশ সাল থেকে আঠারো শো আটষট্টি সাল- এই দীর্ঘকাল যাবত ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে চলেছিলো।
এই সকল আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় যুক্ত হলেন আর একজন সংগ্রামী পুরুষ।
আর একজন সাহসী বীর।
তাঁর নাম- হাজী শরীয়তুল্লাহ!
গর্জে উঠলেন সাহসী সৈনিক
মুসলমানদের অধঃপতন দেখে আঁতকে উঠলেন হাজী শরীয়তুল্লাহ!
অন্ধকার থেকে তাদের আলোর পথে তুলে আনবার জন্যে তিনি ব্যাপকভাবে দীনি দাওয়াতের কাজ শুরু করলেন।
যাবতীয় কুসংস্কার আন্দোলন চালাতে থাকলেন।
সাধারণ মুসলমানকে নৈতিক শিক্ষায় তিনি উদ্বুদ্ধ করে তোলেন। অপরদিকে তিন ইংরেজ এবং অত্যাচারী জমিদার হিন্দুদের বিরুদ্ধেও রুখে দাঁড়ালেন।
তারা ক্ষেপেগেল ভীষণভাবে হাজী শরীয়তুল্লাহর প্রতি।
তবও তাদের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে গর্জে উঠলেন সাহসী সৈনিক- হাজী শরীয়তুল্লাহ
দীর্ঘকাল মক্কায় থেকে হাজী শরীয়তুল্লাহ কেবল কুরআন, হাদীস, ফিকাহ, তাসাউফই শেখেননি, তিনি বিশেষ জ্ঞান অর্জন করেছিলেন ইসলাম, সমাজ বিজ্ঞান ও রাজনীতি সম্পর্কেও।
এ সময়ে তিনি বুঝলেন, ইসলাম কেবল একটি ধর্মের নাম মাত্র নয় বরং একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থার নাম- ইসলাম।
ইসলামের বিস্তারিত ব্যাখ্যা সম্পর্কে অবহিত হবার পর এর প্রচার এবং প্রসারের জন্যে হাজী শরীয়তুল্লাহ নতুনভাবে উদ্যোগী হলেন।
এক মহা আত্ম-প্রত্যয়ের সাথে তিনি নিজের পথকে আবিষ্কার করলেন। আত্মত্যাগ ও আত্মকুরবানীর শিক্ষায় উজ্জীবিত হয়ে তিনি ইসলামের দাওয়াতের কাজ শুরু করলেন ব্যাপকভাবে।
এই দাওয়াতী কাজ শুরু করলেন তিনি তাঁর স্বগ্রামে। স্বদেশে।
আপন-পর-সকল মানুষের মাঝে।
কিন্তু কাজটি ছিলেঅ না খুব সহজসাধ্য। কেননা তখনো তাঁর চারপাশে অশিক্ষা, কুশিক্ষা এবং অপসংস্কৃতির পংকিলে হাবুডুবু খাচ্ছিলো সাধারণ মুসলমান।
তখনকার সামাজিক অবস্থাটা ছিলো অত্যন্ত বেদনাদায়ক।
একদিকে চলছে ধর্মীয় অনাচার, অন্যদিকে রাজনৈতিক অস্থিরতা। আর আছে সাধারণ মুসলমানদের ঘাড়ের ওপর ইংরেজ দস্যু, নীলকর ও অত্যঅচারী হিন্দু জমিদারদের ক্ষিপ্ত শাণিত চাবুক!
আচেতাদের হাতে চকচকে ক্ষুরধার তরবারি!
এর মধ্যে দিয়েই হাজী শরীয়তুল্লাহ নতুনভাবে, নতুন উদ্যমে ঝড়ের মতো এগিয়ে চললেন সামনে।
ক্রমাগত।
ফরায়েজী আন্দোলন
সতেরো শো চৌষট্টি সাল।
মীর কাসিমকে পরাজিত করলো ইংরেজরা।
এরপর থেকে তারা মুসলমানদের ওপর জুলুম-নির্যাতনের মাত্রা আরো বাড়িয়ে দিলো অনেকগুণে।
ইংরেজরা মুসলমানদেরকে সকল দিক দিয়ে ধ্বংস এবং নির্মূল করার জন্যে নানা ধরনের অপকৌশলের আশ্রয় নিলো!
মেতে উঠলো তারা ঘৃণ্য-কুটিল ষড়যন্ত্রে।
ইংরেজরা আক্রমণ করলো মুসলমানদের ধর্ম ও সংস্কৃতির ওপর। তাদের অর্থনীতির ওপর।
মুলমানদের আয়মা, লাখেরাজ বাজেয়াপ্ত হলো।
তাদের হাত থেকে খাজনা আদায়েল ভার ছিনিয়ে নিয়ে তা দিয়ে দিলে অনুগত হিন্দুদের হাতে।
আর এই সুযোগ পেয়ে চরম সাম্প্রদায়িক হিন্দুরা আনন্দে লাফিয়ে উঠলো। বহুদিন যাবত তারাও ওঁৎ পেতে ছিলো সুযোগের অপেক্ষায়।
এমনি একট মোক্ষম অস্ত্রের খোঁজ করছিলো তারা বহুদিন থেকে- যা দিয়ে বহুকালের শত্রু- মুসলমানদেরকে তারা আরো বেশি করে শায়েস্তা করতে পারে।
খাজনা আদায়ের দায়িত্ব পেয়ে হিন্দুরা বিপুল বেগে চড়াও হলো মুসলমানদের ওপর। ইংরেজদের সরাসরি মদদ পেয়ে তাদের সাহসের মাত্রা বেড়ে গেলো হাজার গুণে।
খাজনা আদায়ের অজুহাতে কারণে-অকারণে তারা মুসলমানদের ওপর অত্যাচার নিপীড়ন চালাতে থাকলো অত্যন্ত নির্মমভাবে।
কি ভয়ানক ছিল তাদের সেই অত্যাচার আর নিপীড়ন!
তাদের সেই নির্মম নিষ্ঠুরতার ইতিহাস আলোচনা করতে গেলে এখনো শরীর শিউরে ওঠে!
ভয়ে এবং আতংক কেঁপে ওঠে বুক।
মুসলমানদের অর্থ-সম্পদ, জমি জায়গা ছলে বলে দখল করেও তৃপ্ত হতো না হিন্দুরা।
শারীরিকভাবেও তারা নির্যাতন চালাতো তাদের ওপর।
আর মুসলমানদের ধর্মীয় কাজে বাধা সৃষ্টি করা ছিলো তাদের অন্যতম প্রধান কাজ।
অত্যাচারী হিন্দু জমিদারদের এলাকায় কোনো মুসলমান গরু কিংবা পশু কুরবানী দিতে পারতো না।
দিতে পারতো না মসজিদে আযান।
এমনকি ইসলারেম অন্যান্য হুকুম-আহকামও পালন করতে পারতো না স্বাধীনভাবে।
মুসলমানদের সকল ক্ষেত্রেই বাধা দিতো হিন্দু জমিদাররা।
জমিদারদের সাথে থাকতো পশু স্বভাপের হিংস্র লাঠিয়াল বাহিন।
তারা মুসলমানদের ওপর যখন ঝাঁপিয়ে পড়তো বাঘের মতো।
কি জঘন্য এবং মর্মান্তিক বিষয়!
হিন্দু জমিদাররা এ সময়ে মুসলমানদের দাড়ির ওপরও ট্যাক্স বসিয়ে দিলো!
তাদের ধূতি পরতে বাধ্য করা হতো!
দাড়ি কেটে গোঁফ রাখতে নির্দেশ দিতো!
আর পূজার সময়ে মুসলমানদের কাছ থেকে জোরপূর্বক আদায় করতো চাঁদা, ছাগল, হাঁস-মুরগিসহ পূজার আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র!
এছাড়াও তারা গরীব মুসলমানদের পূজার সময়ে খাটিয়ে নিতো বিনা পারিশ্রমিকে।
যারা তাদের অবাধ্য হতো তাদের ওপর চালাতো নির্মম নির্যাতন।
এভাবেই মুসলমানরা অর্থ এবং ধর্ম হারিয়ে হিন্দুদের হাতে জিম্মি হয়ে পড়েছিলো।
মুসলমানদের ঠিক এই চরম দুঃসময়ে মক্কা থেকে ফিরে এলেন আপন স্বদেশে হাজী শরীয়তুল্লাহ।
তিনি স্বদেশের বুকে পা রেখেই আঁতকে উঠলেন!
চারদিকে তাকিয়ে দেখলেন অবাক বিস্ময়ে!
কেঁপে উঠলো তাঁর দরদ ভরা বুক!
দেখলেন হিন্দু-মুসলমানের আচার আচরণ।
তাদের এই আচার আচরণের মধ্যে খুঁজে পেলেন না হিন্দু মুসলমানের মৌলিক পার্থক্যকারী ইসলামের সেই মহান আদর্শ এবং শিক্ষা।
ইসলামের চর্চা নেই ব্যক্তি কিংবা সমাজ জীবনের কোথাও।
মুসলমানদের কাছে তিনি শুনলেন তাদের সকল দুর্ভাগ্যের কথা।
শুনলেন ইংরেজ এবং হিন্দদের অত্যচারের কথা।
নিজের চোখেও দেখলেন অনেক কিছু।
এসব দেখে আর শুনে ব্যথিত হলেন হাজী শরীয়তুল্লাহ!
ভাগ্যহত মুসলমানদের অন্ধকারের কালো গুহা থেকে টেনে তুলবার জন্যে তিনি সংকল্পবদ্ধ হলেন কঠিনভাবে।
আর তখনই হিন্দু ও ইংরেজদের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠে তাঁর সাহসী কণ্ঠ!
শুরু হলো তাঁর দেশ, জাতি ও ইসলামী আদর্শ-ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারের দুর্বার সংগ্রাম!
সংস্কারের এক কঠিন সংগ্রাম!
হাজী শরীয়তুল্লাহর এই সংগ্রামের নাম, এই আন্দোলনের নাম-‘ফরায়েজী আন্দোলন।’
‘ফরজ’ থেকে ‘ফরায়েজী’। ফরায়েজ শব্দটি বহুবচন।
ফরিজাহ শব্দের অর্থ দাঁড়ায় আলআহর নির্দেশিত অবশ্য কর্তব্যসমূহ। যারা এই কর্তব্যসমূহ পালনে অংগীকারাবদ্ধ তাদেরকে ‘ফরায়েজী’ বলা হয়।
হাজী শরীয়তুল্লাহ সকল আরাম আয়েশ ত্যাগ করে গ্রাম থেকে গ্রামে, শহর থেকেশহরে ঘুড়ে বেড়ান।
এভাবে ঘুরে ঘুরে তিনি সংগ্রহ করেন আপন সংগঠনের জন্যে নিবেদিত কর্মী। সক্রিয় সদস্য।
হাজী শরীয়তুল্লাহ এই আন্দোলনের আগুনকে ছড়িয়ে দেন চারদিকে।
যারা ইসলামের ফরজসমূহ পালন করতে রাজি তারাই কেবল ফরায়েজী আন্দোলনের সদস্য হতে পারতো।
খুব অল্প সময়ের মধ্যে তিনি বিপুল সংখ্যক মুসলমানকে এই আন্দোলনের সদস্য করে তুলেছিলেন।
হাজী শরীয়তুল্লাহ তাঁর সদস্য এবং সাধারণ মুসলমানকে ধর্মের সাথে কর্মের মিল রাখার জন্যে কঠোরভাবে নির্দেশ দিলেন।
আল্লাহর হুকুম-আহকাম মেনে চলার জন্যে তিনি সকলের প্রতি আহ্বান জানালেন। আহ্বান জানালেন শিরক, কুফরী ও বিদআত থেকে দূরে থাকতে।
ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতির আলোকে নিজের জীবনযাত্রা পরিচালনা ও আচার অনুষ্ঠান পালন করার জন্যে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করলেন।
হাজী শরীয়তুল্লাহর আন্দোলন সম্পর্কে জেমস টেইলর বলেন, যে “কুরআনকে অক্ষরে অক্ষরে পালন করাই ছিলো ফরায়েজী আন্দোলনের উদ্দেশ্য।
কুরআন যেসব অনুষ্ঠানাদি সমর্থন করে না তা সবই ছিলো বর্জনীয়।
মহররমের অনুষ্ঠান পালনই শুধু নিষিদ্ধ ছিলো না, এ অনুষ্ঠানের ক্রিয়াকলাপ দেখাও ছিলো তাদের জন্যে নিষিদ্ধ।”
যেখানে পশু কুরবানী দেয়াই ছিল, সেখানে হিন্দুদের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে হাজী শরীয়তুল্লাহ নিজেই গরু কুরবানী দিলেন।
সবাই অবাক- বিস্ময়ে দেখলো হাজী শরীয়তুল্লাহর সাহস।
তাঁর এই সাহসে অন্য মুসলমানও উদ্বুদ্ধ হলো।
এরপর তিনি অন্যান্য মুসলমানকেও গরু কুরবানী দিতে বললেন।
দাড়ির ওপর ট্যাক্স দিতেও মুসলমানদেরকে কঠোরভাবে নিষেধ করলেন। আর শক্তভাবে নিষেধ করলেন হিন্দুদের পূজা পার্বণে চাঁদা বা পশু পাখি দিতে। হিন্দু জমিদারদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে তিনি আরো বেশী সোচ্চার হলেন। চারকিকে শুরু হয়ে গেলো তুমুল আন্দোলন!
হাজী শরীয়তুল্লাহর এই সাহসী আন্দোলন ছিলো সত্যের পক্ষে আর অন্যায়ের বিরুদ্ধে।
হাজী শরীয়তুল্লাহর এই সাহসীকর্ম তৎপরতায় ক্ষেপে গেলো অত্যাচারী হিন্দুরা।
ক্ষেপে গেলো হিন্দু জমিদার এবং ইংরেজরাও।
চারদিকে শুরু হয়ে গেলো সংঘর্ষ!
সংঘর্ষ হলো তাদের জায়গায়!
কিন্তু পিছু হটলো না ফরায়েজীর সিংহদিল কর্মীরা!
যতোই বাধা আসতে থাকলো, ততোই বিদ্যুৎগতিতে ছড়িয়ে পড়তে থাকলো ফরায়েজী আন্দোলনের তীব্র আগুন।
শত বাধার মুখেও হাজী শরীয়তুল্লাহ ছিলেন অনড় এক পর্বত!
আর তাঁর সাথীরাও ছিলো তেমনি সত্যের পথের এক একজন সিংহপুরুষ!
হাজী শরীয়তুল্লাহ ছিলেন হানাফী মাজহাবের অনুসারী এবং সেই সাথে বাংলাভাষী।
পারিবারিকভাবে ক্ষুদ্র তালুকদার হলেও শেষ পর্যন্ত সেটাও ছিল না।
তিনি যখন হজ পালন করে বাড়ি ফেরেন, তখন তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা তেমন ভাল ছিল না।
অন্যদিকে মুসলমান সমাজের উঁচু দরের বা আশরাফ হিসেবেও পরিচিত ছিলেন না।
তাতে কি
তবুও মধ্যম গড়নের, দীর্ঘ দাড়ি সম্বলিত হাজী শরীয়তুল্লাহ ছিলেন বাঙালি মুসলমানের জন্য প্রকৃত ইসলামী সমাজ সংস্কারের একজন রূপকার।
তাই সাধারণ মানুষের মাছে তাঁর মিশে যাওয়া খুব অসুবিধা হয়নি। বরং সাধারণ মানুষ তাঁর বুকে ঠাঁই পেয়েছে। পেয়েছে মাঝে একজন আপন লোক। তার ওপর তিনি ইসলামের পুণ্যভূমি মক্কায় দীর্ঘদিন অবস্থান করে অনেক কিছু শিখেছেন। তাঁর সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন চরিত্র সাদামাঠা জীবন অমায়িক ব্যবহার, আন্তরিক, প্রয়াস, সবাইকে সমান মর্যাদা প্রদানের অঙ্গীকার- যে কাউকে মোহিত ও মুগ্ধ করার জন্য ছিল যথেষ্ট।
এমন একজন অনুকরণ ও অনুসরণযোগ্য নেতাই তখনকার পরিবেশে প্রয়োজন ছিল অনেক বেশী।
সাধারণ মানুষের সমস্যা তিনি বুঝতেন এবং কিভাবে তার সমাধান করা যায়, তাও জানা ছিল তাঁর। ফলে তিনি সহজেই একটি গতিশীল আন্দোলন সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন।
ফলে সেই সময়ে অনেক আন্দোলন সৃষ্টি হলেও ফরায়েজী আন্দোলনই হয়ে উঠেছিল সবচেয়ে কার্যকর, ফলপ্রসূ এবং স্থায়ী।
ইংরেজ সিভিলিয়ন জেম টেলর তা ‘A Sketch of the Topography and statistics of Dacca’ তে লিখেছেন,
“১৮২৮ সালের পর থেকে ফরায়েজী আন্দোলন ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত হচ্ছে।”
অন্যদিকে জেমস ওয়াইজের মতে,
“শিরক ও বিদআত থেকে স্থানীয় মুসলমানদের রক্ষা করার ক্ষেত্রে হাজী শরীয়তুল্লাহই পূর্ববঙ্গের ইসলামের প্রথম সংস্কারক ও প্রচারক।”
সুতরাং এ থেকেই বুঝা যায়, ইসলামের জন্য হাজী শরীয়তুল্লাহর অবদানটা কত বেশী!
একজন অভিভাবকের কথা
হাজী শরীয়তুল্লাহ বাংলার মুসলিম সমাজে একজন অভিভাবকের ভূমিকা পালন করতেন।
বিপদে মুসিবতে, সুখে-দুঃখে তিনি তাদের পাশে এসে দাঁড়াতেন।
তিনি ছিলেন তাদের জন্যে একজন দরদী অভিভাবক ও পরামর্শদাতা।
হিন্দু জমিদার ও ইংরেজ ব্যবসায়ীদের অত্যাচার-নিপীড়নের বিরুদ্ধে মুসলিম জনগণকে হাজী শরীয়তুল্লাহ ঐক্যবদ্ধ করে তোলেন।
তিনি হিন্দু জমিদারদের অনেক অবৈধ কর আদায়ের বিরোধিতা করেন।
অবৈধ কর না দেবার জন্যে হাজী শরীয়তুল্লাহ মুসলিম জনগণকে নির্দেশ দিয়েছিলেন কঠিনভাবে।
হাজী শরীয়তুল্লাহ একদিকে রাজনৈতিকভাবে ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হন। আর অপরদিকে সামাজিকভাবে তিনি অত্যাচারী হিন্দু জমিদার ও নীল কুঠিয়ালতের বিরোধিতায় অবতীর্ণ হন।
সেই সাথে বেগবান রাখেন তিনি মুসলমানদের মধ্যে শিরক, বিদআত ও কুসংস্কার দূর করার জন্য সংস্কারের এক মহা বিপ্লবের ধারা।
শরীয়তুল্লাহর এই সংগ্রাম অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। ছড়িয়ে পড়ে গ্রাম থেকে গ্রামাঞ্চলে। বাংলার প্রতিটি ঘরে ঘরে।
ফড়িয়ে পড়ে ফরিদপুর, বরিশা, খুলনা, যশোর, কুষ্টিয়া, ঢাকা, ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা প্রভৃতি জিলায়ও।
তাঁর এই সংগ্রামে যুক্ত হয়েছিলো সমাজের প্রধানত দরিদ্র কৃষক শ্রেণী। যারা হিন্দু জমিদার ও ইংরেজদের অত্যাচার আর শোষণের শিকার ছিলো। হাজী শরীয়তুল্লাহ তাদের ঐক্যবদ্ধ করেন। ঐক্যবদ্ধ করলেন তিনি অসহায়, নিঃস্ব ভাগ্যহত মানুষকে।
তাদেরকে শুনালেন তিনি আশার বাণী।
আঠারো শো সাইত্রিশ সালে তাঁর এই সংগ্রামী আন্দোলনের সদস্য সংখ্যা ছিলো প্রায় বারো হাজারের মতো।
কম কথা!
এই বিপুল সংখ্যক সদস্যের বাইরেও ছিলো একটি বিশাল জনশক্তি।
যারা তাঁর আন্দোলনকে সকল সময় সমর্থন ও সহযোগিতা করতো।
হাজী শরীয়তুল্লাহ ছিলেন প্রকৃত অর্থেই দুঃখী মানুষের জন্যে একজন দায়িত্বশীল অভিভাবক।
গরীবের কষ্ট তিনি সইতে পারতেন না কখনো।
তাই তিনি সকল সময়ই তাদের পাশেগিয়ে দাঁড়াতেন।
এমন জন-দরদী নেতার অভাব ছিল তখন।
হাজী শরীয়তুল্লাহ সময়ের সেই দাবি ও চাহিদা পূরণে তাঁর সর্বশক্তি নিয়োগ করেন।
কৌশলী কর্মপন্থা
খুবই সতর্কতার সাথে হাজী শরীয়তুল্লাহ তাঁর আন্দোলন ও সংস্কারের কর্মপন্থা নির্ধারণ করেছিলেন।
স্থানীয় জমিদার এবং ইংরেজদের সাথে যাতে কোন ধরনের সংঘর্ষ না বাধে, সে ব্যাপারে তিনি সতর্ক ছিলেন।
তিনি নীরবে তাঁর কাজ চালয়ে যাচ্ছিলেন। ফলে দিন দিন তাঁর অনুসারী সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছিল।
কৃষক, তাঁতিসহ সাদারণ মানুষকে হাজী শরীয়তুল্লাহর অধীনে সংঘবদ্ধ হতে দেখে জমিদাররা আতঙ্কিত হতে থাকে।
আগে হিন্দু জমিদাররা তাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে মুসলমান প্রজাদের নিকট থেকে টাকা পয়সা আদায় করতো।
অথচ এটা ছিল ঈমানের সাথে সাংঘর্ষিক।
হাজী শরীয়তুল্লাহ হিন্দুদের পূজার চাঁদা দিতে নিষেধ করেন।
হিন্দু জমিদারদের প্রমাগ গোণার এটাও একটা কারণ ছিল।
এছাড়া এতোদিন মুসলমানরা বিচ্ছিন্ন থাকায় তারা যে কোন ধরনের অত্যাচার করতে পারতো। এবার সেই পথও তাদের বন্ধ হবার উপক্রম হলো। তবু তারা নানাভাবে মুসলমানদের হয়রানি করতে থাকে।
তাই জীবনের শেষ দিকে শক্তি প্রয়োগের কথা ভাবতে থাকেন হাজী শরীয়তুল্লাহ। তারই ফলে দুদু মিয়ার সময় জমিদারদের সাথে সংঘর্ষ হয়েছিল। তবে দুদু মিয়াও বেশ কৌশলে সবদিক মুকাবিলা করেছিলেন। দুদু মিয়া জমিদার এবং নীরকরদের বিরুদ্ধে দুর্বার গতিতে লড়াই করেছেন। তাঁর নেতৃত্বে বাঙালি মুসলমানরা জমিদারদের বিরুদ্ধে সফলতা লাভ করে। এর আগে সাইয়েদ নিসার আলী তিতুমীর জমিদার ও ইংরেজদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ [১৮২৭-১৮৩১] করেছিলেন। কিন্তু তা ব্যর্থতায় রূপ নেয়।
তবে দুদু মিয়া অনেক বেশি সফলতা পেয়েছিলেন।
সরকারের সাথে প্রকাশ্যে বিরোধিতায় না জড়িয়ে প্রথমশত্রু অর্থাৎ জমিদারদের তিনি ঠিকই শায়েস্তা করেছিলে। প্রশাসনিক এবং আইনী সুযোগও তিনি পুরোপুরিভাবে কাজে লাগাবার চেষ্টা করেছেন।
সেই সময়ে আন্দোলনগুলো বা ব্যক্তি মতাদর্শ প্রচারের জন্যে প্রায়ই বহাস নামে বিতর্ক সভার আয়োজন করা হতো।
আর এগুলোর প্রায়ই সমাপ্ত হতো মারামারির মাধ্যমে।
সমস্যার মীমাংসা হওয়ার চাইতে সমস্যা আরো গুরুতর রূপ ধারণ করতো। তাই হাজী শরীয়তুল্লাহ সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়েছিলেন এ ধরনের বিরোধ এড়াতে। তিতুমীর এবং তারিখে মোহাম্মদীর পাটনা গ্রুপের সাথে হাজী শরীয়তুল্লাহর সম্পর্ক ভাল ছিল।
তিনি তাদের আন্দোলনে যোগ না দিলেও পারস্পরিক বিরোধ থেকে তাঁরা সবাই মুক্ত ছিলেন।
মাওলানা কেরামত আলীর আন্দোলনও একই সময়ে পরিচালত হয়েছিল। আহলে হাদীস আন্দোলনও সেই সময় একটু জোরে শোরে শুরু হয়েছিল। মাওলানা কেরামত আলী জৌনপুরি বাঙলায় আসেন ১৮৩৫ সালে।
১৮৭৩৪ সালে ইন্তেকালের পূর্ব পর্যন্ত তিনি বাংলায় ইসলাম প্রচারে নিমগ্ন ছিলেন।
ফরায়েজী আন্দোলনের সাথে তাঁর মূল বিরোধ ছিল ঈদ এবংজুআর নামাজ আদায় না করা এবং খুঁটিনাটি আরো কিছু বিষয়ে।
মাওলানা কেরামত আলী সমাজে প্রচলিত অনেক ব্যাপারে নমনীয় হয়ে কিছুটা ছাড় দেয়ার পক্ষপাতী ছিলেন।
তারিখে মোহাম্মদ আন্দোলন ধর্মীয় আন্দোলন হিসেবে শুরু হয়েছিল ১৮১৮ সালে।
কয়েক বছরের মধ্যেই তা রাজণৈতিক আন্দোলন রূপ নেয়।
কিন্তু নিম্ন বাংলার কৃষক সমাজের কাছে সেটা তেমন সাড়া জাগাতে পারেনি। সাইয়েদ আহমদ শহীদের আন্দোলন দিনাজপুর, মালদহ, রাজশাহী, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, বর্ধমান, যশোর, কলকাতা এবং চব্বিশ পরগনায় জোরালো ছিল। অর্থাৎ গঙ্গা এবং ভাগিরথি নদীর দু’কূলে ছিল তাদের প্রচার ভূমি।
একই সময়ে এতগুলো সংস্কার আন্দোলন ও শোষণ-নিপীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রাম অব্যাহত ছিল।
কিন্তু কোনো নেতা অন্যের আন্দোলনকে অবজ্ঞা করেননি।
লিপ্ত হননি সরাসরি কোনো বিরোধিতায়।
হাজী শরীয়তুল্লাহ এই সময় অত্যন্ত কৌশলী কর্মপন্থা গ্রহণ করেন।
দারুল হরব
হাজী শরীয়তুল্লাহ যখন মক্কায় চিলেন, তখন তাঁর পরিচয় ঘটে মক্কার মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাব নজদর ইসলামী সংস্কার আন্দোলনের সাথে। এই আন্দোলনের প্রতি হাজী শরীয়তুল্লাহ আকৃষ্ট হযে পড়েন।
দিল্লিতে শাহ আবদুল আযীয দেহলভীর নেতৃত্বে ভারতেও আবদুল ওয়াহ্হাব নজদীর অনুকরণে ইসলামী সংস্কার আন্দোলন শুরু হয়।
তিনি ভরবর্ষকে ‘দারুল হরব’ বলে ঘোষণা করেন।
‘দারুল হরব’ কে ‘দারুল ইসলাম’ তথা একটি ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্যে যাঁরা অক্লান্তভাবে চেষ্ট করেছিলেন।
তাঁদের মধ্যে ছিলেন সাইয়েদ আহমদ বেরেলভী,শাহ আবদুল আযীযের ভ্রাতুষ্পুত্র শাহ ইসমাইল ও জামাতা মাওলানা আবদুল হাই।
হাজী শরীয়তুল্লাহও এদেশকে ‘দারুল হরব’ ঘোষণা করেন।
তিনি ঘোষণা দেন, এদেশ যতোদিন ‘দারুল ইসলাম’ না হবে, ততোদিন এখানে ‘জুমআ’ ও ঈদের নামায হবে না।
হাজী শরীয়তুল্লাহ এদেশে যেমন ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্যে চেষ্টা করেছেন, ঠিক তেমনি অন্য দেশেও ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্যে তাঁর অবদান ছিলো অসামান্য।
তিনি সাইয়েদ আহমদ বেরেলভীর ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের কাজে সহায়তা করার জন্যে এদেশ থেকে বহু মুজাহিদ এবং যাকাত, ফিতরা থেকে সংগৃহীত অর্থসহ নানা ধরনের সাহায্য ভাতের সিত্তানা কেন্দ্রে পাঠাতেন।
জুলুম নির্যাতন
যে কোনো ভালো কাজ করতে গেলেই দুষ্ট লোকেরা বাধ সাধে। বাধ সাধে এজন্যে যে, তাদের স্বার্থে আঘা লাগে।
হাজী শরীয়তুল্লাহও বিনা বাধায় কাজ করতে পারেননি।
তাঁর আন্দোলনী জীবনে বারবার বাধা এসেছে। বাধা এসেছে জমিার ও ইংরেজদের পক্ষ থেকে।
তাঁর কর্মীদের পুলিশ নির্মমভাবে অত্যাচার করেছিলো।
তাঁকেও সইতে হয়েছিলো নানা ধরনের নিপীড়ন। তাঁকে রামনগর থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিলো।
আঠারো ঊনচল্লিশ সাল পর্যন্ত তাঁকে বেশ কয়েকবার গ্রেফতারও করা হয়েছিলো।
কিন্তু কোনোভাবেই হিন্দু জমিদার এবং ইংরেজরা পরাস্ত করতে পারেননি সত্যের সৈনিক হাজী শরীয়তুল্লাহকে।
বরং তাদের পক্ষ থেকে যতোই বাধা আসতো ততোই তিনি তাঁর সংগ্রামী ভূমিকা পালন করে যেতেন দুর্বার গতিতে।
সামনে এগিয়ে যেতেন দিগুণ সাহসের সাথে।
হাজী শরীয়তুল্লাহর নতুন কর্মক্ষেত্র ছিলো ঢাকা জিলার নয়া বাড়িতে।
কিন্তু হিন্দু জমিদারদের চরম বিরোধিতার ফলে তিনি ঢাকার নয়া বাড়ি ছাড়তে বাধ্য হন।
এখান থেকে ফিরে যান তিনি তাঁর নিজের গ্রাম- শামাইলে।
সেখানে থেকেই হাজী শরীয়তুল্লাহ পূর্ণ গতিতে ফরায়েজী আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতে থাকেন।
অত্যাচারী হিন্দু জমিদার, নীল কুঠিয়াল এবং ইংরেজ দস্যুরা আরো বেশি ক্ষেপে গেলো হাজী শরীয়তুল্লাহর ওপর।
জুলুম-অত্যাচার ছাড়াও হাজী শরীয়তুল্লাহ এবং তাঁর আন্দোলন সম্পর্কে সে সময়ে বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হলো না প্রকার কল্পকথা।
যেসব কথার কোনো ভিত্তিই ছিলো না।
তাতে ছিলো না সত্যের লেশ মাত্র।
এখানে মাত্র একটি উদাহরণ দিলেই ব্যাপারটি বুঝা যাবে সহজে।
পত্র-পত্রিকার ভাষ্য
হিন্দু যে ফরায়েজী আন্দোলনকে মোটেই সহ্য করতে পারতো না তা বুঝা যায় তাদের পত্রিকা ‘সমাচার দর্পণের’ ভাষ্য থেকেই।
আঠারো শো সাইত্রিশ সালের বাইশে এপ্রিল তারিখে এই পত্রিকায় একটি পত্র ছাপা হয়। পত্রটি ছিলো এ রকম:
“ইদানিং জিলা ফরিদপুরের আন্তঃপিাতি শিবচর থানার সরহদ্দে বাহাদুরপুর গ্রামে সরিতুল্লাহ নামক একজন বাদশাহী লওনেচ্ছুক হইয়া ন্যূনাধিক বার হাজার জোলা ও মুসলমান দলবদ্ধ করিয়া নতুন এক সরা জারি করিয়া নজ মতাবলম্বী লোকদিকের মুখে দাড়ি, কাছা খোলা, কটি দেশের ধর্মের রুজ্জুভৈল করিয়া তৎতুর্গিস্থ হিন্দুদিগের বাড়ি চড়াও হইয়া দেবদেবী পূজার প্রতি অশেষ প্রকার আঘাত জন্মাইতেছে- এই জিলা ঢাকার অন্তঃপাতি মতলবগঞ্জ থানার রাজনগর নিবাসী দেওয়ান মৃত্যুঞ্জয় রায়ের স্থাপিত দ্বাদশ শিবলিঙ্গ ভাঙ্গিয়া নদীতে বিসর্জন দিয়াছে এবং ঐ থানায় সরহদ্দে দ্বাদশ শিবলিঙ্গ ভাঙ্গিয়া নদীতে বিসর্জন দিয়াছে এবং ঐ থানার সরহদ্দে পোড়াগাছা গ্রামে একজন ভদ্রলোকের বাটিতে রাত্রিযোগে চড়াও হই সর্বস্ব হরণ করিয়া তাহার গৃহে অগ্নি দিয়া অবশিষ্ট যেটুকু ছিল ভষ্ম রাশি করিলে একজন যবন মৃত হইয়া ঢাকায় দাওরায় অর্পিত হইয়াছে।
... আর শ্রত হওয়া গেল, সরিতুল্লাহ দলভুক্ত দুষ্ট যবনের ঐ ফরিদপুরের অন্তঃপাতি পাটকান্দা গ্রামের বাবু তারিনী চরণ মজুমদারের প্রতি নানা প্রকার দৌরাত্ম্য অর্থাৎ তাহার বাটিতে দেবদেবী পূজায় আঘাত জন্মাইয়া গোহত্যা ইত্যাদি কুকর্ম উপস্থিত করেলে মজুমদার বাবু যবনদিগের সহিত সম্মুখ যুদ্ধ অনুচিত বোধ করিয়া- ঐ সকল দৌরাত্ম্য ফরিদপুরের ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের হুজরে জ্ঞাপন করিলে ঐ সাহেব বিচারপূর্বক কয়েকজন যবনকে কারাগারে বদ্ধ করিয়াছেন এবং এ বিষয়ে বিলক্ষণ অনুসন্ধান করিতেচেন। সে সম্পাদক মহাশয়, দুষ্ট যবনেরা মফঃস্বলে এ সকল অত্যাচার ও দৌরাত্ম্যে ক্ষান্ত না হইয়া বরং বিচার গৃহে আক্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। শ্রুত হওয়া গেল, ফরিদপুরের ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের হুজরে যে সকল আমলা ও মোক্তার-কারেরা নিযুক্ত আছে, তাহারা সকলেই সরিতুল্লাহ যবনের মতাবলম্বী- তাহাদের রীতি এই যদি কাহার নামে মিথ্যা অভিযোগ করিতে হয়, তবে কেহ ফরিয়াদী কেহ বা সাক্ষী হইয়া মোকদ্দমা উপস্থিত করে সুতরাং ১২০০০ লোক দলবদ্ধ। ইহাতে ফরিয়াদীর সাক্ষীর ত্রুটি কি আছে... আমি বোধ করি, সরিতুল্লাহ যবন যে প্রকার দলবদ্ধ হইয়া উত্তর উত্তর প্রবল হইতেছে অল্পদিনের মধ্যে হিন্দু ধর্ম লোপ পাইয়া অকালে প্রলয় হইবেক। সরিতুল্লাহর চোটপাটের শত অংশের এক অংশ তিতুমীর করিয়াছিল না। ইতি সন ১২৪৩ সাল, তারিখ ২৪শে চৈত্র।”
সুতরাং এই একটি মাত্র চিঠির মাধ্যমেই পরিষ্কার হয়ে যায় যে, হাজী শরীয়তুল্লাহকে কত ভাবে আক্রমণ করা হয়েছিল!
তাতে কি!
সাহসী সৈনিক কি থেমে যায় কখনো? না!
হাজী শরীয়তুল্লাহও থেমে থাকেননি।
বরং তিনি অত্যন্ত সাহসিকতা ও দৃঢ়তার সাথে সকল বাধা ও প্রতিবন্ধকতা মুকাবিলা করে ক্রমাগত এগিযে গেছেন সামনের দিকে। ক্রমাগত সামনের দিকেই।
সমাজ সংস্কারক
দীর্ঘদিন হিন্দুদের সাথে মিলে মিশে এবং তাদের পাশাপাশি থাকার কারণে এবং যথাযথ ধর্মীয় বোধ না থাকার কারণে মুসলমানদের মধ্যে হিন্দু সমাজের অনেক রীতি নীতি ও ধ্যান ধারণা প্রবেশ করেছিলো।
যা ছিলো ইসলামের আকীদা বিশ্বাসের সম্পূর্ণ বিপরীত।
ছিল শিরক বিদআত পর্যায়ের।
হাজী শরীয়তুল্লাহ শরক বিদয়াত, পীর-ফকিরের মাজারে সিজদা, মানব ও হিন্দুদের পূজার মতো নানা খারাবী ও বাড়াবাড়ি ইসলামের মৌলনীতি কুরআন ও হাদীসের বিপরীত বলে ঘোষণা করেন।
তিনি সকল মুসলমানকে এসব কাজ থেকে বিরত থাকার জন্যে জোর আহ্বান জানান।
হাজী শরীয়তুল্লাহই এদেশে প্রথম শরীয়ত, তরীকতের ধারক ও বাহক পীরদের মর্যাদা সম্পর্কে মানুষকে জানান।
তাঁদের সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে বলেন যে, তাঁরা শিক্ষকের মতো। এর বেশি কিছু নয়।
অতেএব তাঁদেরকে শ্রদ্ধা করা যায়, কিন্তু এর বেশি আর কিছু করা যাবে না। অথচ তখনকার মুসলমানদের ধারণা ছিল যে, পীরেরা তাদের মুরীদানকে আল্লাহর কাছে সুপারিশ করে জান্নাতে নিয়ে যেতে পারবেন।
তাই অনেক মুরীদ খারাপ কাজে লিপ্ত থাকতো।
তারা ঠিকভাবে আল্লাহর হুকুম মেনে চলতো না।
তাদের বিশ্বাস ছিলো আমল এবং আখলাকে ঘাটতি থাকলেও পীর সাহেব তাদেরকে পার করে দিতে পারবেন।
জান্নাতে যাবার জন্যে যা যা দরকার তিনি সব বন্দোবস্ত করে দেবেন। কি সর্বনেশে চিন্তা!
হাজী শরীয়তুল্লাহ তাদের এইসব ভুল ধারণা ভেঙ্গে দেন।
হাজী শরীয়তুল্লাহ বিবাহ এবং অন্যান্য সামাজিক উৎসবগুলোতে অযথা খরচ করার বিরোধিতা করেন।
মুসলমান জাতির আর্থিক উন্নয়নের জন্যে তিনি বিশেষভাবে সচেষ্ট ছিলেন। আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ভয় না করার জন্যে তিনি সকেলর প্রতি আহ্বান জানান।
কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী সকল কাজ সম্পাদন করার জন্যে তিনি সকলকে নির্দেশ দেন।
হাজী শরীয়তুল্লাহকে এক সাথে অনেকগুলো শক্তিকে মুকাবিলা করতেহয়েছে। জাঁকিয়া বসা পীর তন্ত্র, নানা মারমী তরীকা, শিয়া মাজহাব, মাওলানা কেরামত আলীর আন্দোলন এবং সর্বোপরি স্থানীয় জমিদার এবং ইংরেজ শাসকবৃন্দকে তাঁকে শক্তভাবে মুকাবিলা করতে হয়েছে।
পীর ব্যবস্থাটি বাংলার মুসলমান সমাজে এতো গভীরভাবে প্রবেশ করেছিল যে, আত্ম-মর্যাদাবান জাতি হিসেবে অস্তিত্ব ঘোষণার জন্য সেই সময়ে এই প্রভাব থেকে বেরিয়ে আসা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ।
এদশে ইসলাম প্রচার ও প্রসারে পীর দরেবেশদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। বলতে গেলে তখনকার দিনে ধর্মীয় বিধি বিধান সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জনের প্রধান মাধ্যমই ছিল তাঁরা।
কিন্তু ঊনবিংশ শতকের ঘোর অমানিশার সময়ে পীর-দরবেশ নামে অনেকেই বিভ্রান্ত ছড়াতো।
তাছাড়া মৃত অনেক পীরের নামে মানত করা, তাদের মাজারে শিরনি দেওয়ার রেওয়াজ ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল্
পাঁচ পীর, মানিক পীর, ঘোড়া পীর, মাদারী পীর, খাজে খিজির, জিন্দা গাজী, বদর পীর প্রমুখের প্রতি শিরনি বা মানত না করে কেউ কোনো কাজে হাত দিত না।
পীর ভক্তি তখন শিরকের পর্যায়ে চলে গিয়াছিল।
মুসলমানদের এই বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত করা ছিল খুবই প্রয়োজনীয় একটি কাজ। তাই হাজী শরীয়তুল্লাহ এক্ষেত্রে ইসলামী চেতনার বিস্তার ঘটান।
পীর, সুফি, শেখ প্রভৃতি মাধ্যম বাদ দিয়ে আল্লাহর সাথে বান্দার সরাসরি সম্পর্কের কথা প্রচার করলেন।
শিক্ষার জন্যে কোনো মাধ্যম অবশ্যই প্রয়োজন।
তাই তিনি উস্তাদ-শাগরেদ ব্যবস্থা কায়েম করে নতুন দিগন্তের সূচনা করলেন। অবশ্য পরবর্তীকালে অনেকটা পীরদের মতোই তাঁর বংশধররাই ফরায়েজী আন্দোলনের প্রধান নির্বাচিত হতেন।
তবে এক্ষেত্রে আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের মতামত প্রয়োজন হতো।
হাজী শরীয়তুল্লাহ জানিয়ে দিলেন, সত্যিকারের মুসলমান হওয়ার জন্য কোনো পীর দরবেশের প্রয়োজন নেই।
জাঁকজমকপূর্ণ কোনো অনুষ্ঠানেরও দরকার নেই।
আল্লাহ ও তাঁর নবীকে (সা) স্বীকার তথা তৌহিদ ও রিসালাতে বিশ্বাস এবং ফরজ পালনের মধ্যেই যাবতীয় মুক্তি নিহিত রয়েছে।
এভাবে হাজী শরীয়তুল্লাহ মানুষকে সঠিক পথের সন্ধান দেন।
অন্যায় জুলুমরে বিপরীতে তিনি সকল মানুষকে এক হবার জন্যে তাকিদ দেন।
তাঁর এ মুক্তির আহ্বানে সাড়া দিয়ে মুসলমানরা সেদিন সংগ্রাম ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো।
হাজী শরীয়তুল্লাহর সংস্কার তথা ফরায়েজী আন্দোলন মূলত রাজ্যহারা, সম্পদহারা মুসলিম জাতির মনের আশা ও ভরসা এনে দিয়েছিলো।
তাঁর এ আন্দোলনের জন্যে যেন হাজার হাজার মুসলমান বহুদিন থেকে অপেক্ষায় প্রহর গুণছিলো।
সেই সুযোগ যখন এলো, তখন তাঁর কথায় এক সাথে সকলেই জেগে উঠলো অসহায় মুসলমানের মুক্তির জন্যে।
কম বিস্ময়ের ব্যাপার নয়!
অত্যাচারী জমিদারদের বিরুদ্ধে তারাও সোচ্চার হয়ে ওঠে হাজী শরীয়তুল্লাহর নেতৃত্বে।
ঝাঁপিয়ে পড়ে তারা সকল প্রকার ত্যাগ স্বীকার করে।
হাজী শরীয়তুল্লাহর এই সংস্কার প্রচেষ্টা বিফলে যায়নি। যাবার কথাও নয়।
সত্যিই একদিন তাঁর ফরায়েজী আন্দোলন সফলতার দ্বাপ্রান্তে উপস্থিত হয়েছিলো।
এ সম্পর্কে জেম্স ওয়াইজ তাঁর মোহামেডানস অব ইস্টার্ণ বেঙ্গল’ গ্রন্থে বলেন:
“হিন্দুদের বহু ইশ্বরবাদ নীতির সাথে দীর্ঘদিনের সম্পর্কের ফলে মুসলমানদের মধ্যে যেসব কুসংস্কার ও দুর্নীতি দেখা দিয়েছিল তার বিরুদ্ধে কথা বলার প্রথম সোচ্চার প্রচারক হিসেবে তাঁর [হাজী শরীয়তুল্লাহ] আবির্ভাব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। কিন্তু বাংলার চেতনাহীন ও উদাসীন চাষী সমাজের মধ্যে তিনি উৎসাহ-উদ্দীপনা জাগ্রত করার ব্যাপারে যে সাফল্য অর্জন করেন, তা আরও বেশী চমকপ্রদ।
এ উদ্দেশ্যে সাধনের জন্যে একজন অকপট ও সহানুভূতিসম্পন্ন প্রচারকেরই প্রয়োজন ছিল। আর মানুষের মনে প্রভাব বিস্তারের অধিকতর ক্ষমতা শরীয়তুল্লাহর চেয়ে অপর কারুর মধ্যে কখনও দেখা যায়নি।”
হাজী শরীয়তুল্লাহ ছিলো উন্নত চরিত্র। ছিলো তাঁর অতুলনীয় মানবীয় গুণ ওবৈশিষ্ট্য।
সেই চমৎকার আকর্ষণীয় এবং মোহনীয় শক্তি ছিলো তাঁর। আর এজন্যই তাঁর চরিত্রে মুগ্ধ ছিলো হাজার হাজার মুসলমান।
আদর্শ ও চরিত্রের গুণেই তিনি জয় করেছিলেন ভাগ্যহত মানুষের মন।
তাঁর নির্মল চরিত্রের প্রশংসা করতে গিয়ে ডক্তর ওয়াইজও বলতে বাধ্য হয়েছেন যে,
“তাঁর নির্দেশ ও আদর্শ চরিত্র দেশবাসীদের ভক্তিশ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। দুর্যোগের দিনে সৎ পরামর্শ ও ব্যথা-বেদনায় সান্ত্বনা প্রদানকারী পিতার মতোই দেশের জনগণ তাঁকে ভালোবাসতেন।”
প্রকৃত অর্থেই হাজী শরীয়তুল্লাহ ছিলেন একজন নির্ভীক ও নিবেদিত-প্রাণ সমাজ সংস্কারক।
এদেশের মুসলমানদের চরম দুর্দিনে তিনি যোগ্য অভিভাবকের মতো তাদের কাছে টেনে নিয়েছিলেন।
দেখিয়েছিলেন সত্য-সঠিক পথ।
এজন্যই ইতিহাসের পাতায় এখনো জ্বল জ্বল করে আছে তাঁর নাম- হাজী শরীয়তুল্লাহ!
হান্টারের পরিচয়
হান্টারের পুরো নাম ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার।চাকরি কতেন বৃটিশের অধীনে।
তিনি ছিলেন বৃটিশের একজন পদস্থ রাজকর্মচারী।অন্যান্য ইংরেজদের মতো হান্টারও ছিলেন মুসলমানদের বিদ্রোহের ঘোর বিরোধী। মুসলিম বিদ্ধেষী তো বটেই। হান্টারের যোগ্যতা ছিলো লেখায়।
তিনি ভালো লিখতে পারতেন। তার এই যোগ্যতার কারণে ইংরেজ তাকে দায়িত্ব দিয়েছিলো মুসলমানদের বিদ্রোহ সম্পর্কে গোপন তথ্য সংগ্রহের। তার বিশেষ দায়িত্ব ছিলো সৈয়দ আহম শহীদের আন্দোলনের ওপর রিপোর্ট তৈরি করে বৃটিশ সরকারের কাছে পেশ করা।
ইংরেজের দেয়া এই দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে হান্টার তৎকালীন মুসলমানদের আন্দোলন ও বিদ্রোহ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। ‘দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস্’ নামে একটি গ্রন্থও তিনি লেখেন।
এই গ্রন্থে হান্টার বিভিন্ন জায়গায় মুসলমানদের আন্দোলন ও বিদ্রোহ সম্পর্কে তীর্যক-তীক্ষ্ম ভাষায় অনেক কিছুর উল্লেখ করেছেন।
হান্টার মুসলমানদের কোনো বন্ধু ছিলেন না।
তিনি তার দায়িত্ব পালনের জন্যে মুসলমান ও তাদের আন্দোলন সম্পর্কে যা আলোচনা করেছেন তা মুসলমানদের কল্যাণের জন্য করেননি।
করেছেন ইংরেজদের হুকুম পালন করার জন্যে।
তাদের তুষ্টির জন্যে।
তবুও তার এই পর্যালোচনা রিপোর্ট এবং তার মতামতের মধ্যে মুসলমানদের শৌর্য, সাহস ও আন্দোলন তৎপরতা সম্পর্কে হান্টার যে তথ্য পরিবেশন করেছেন তা আমাদের জন্যে আজো রীতিমত বিস্ময়ের ব্যাপার! তার অনেক সত্য উচ্চারণের মাধ্যমে আমরা সেই সময়কার একটি চালচিত্র পেয়ে যাই।
এখানে হান্টারের কয়েকটি অভিমত উপস্থাপানের মধ্য দিয়ে তখনকার আন্দোলন-বিদ্রোহ সম্পর্কে আমরা কিছুটা ধারণা লাভ করবো।
হান্টারেরর অভিমত
‘দি ইন্ডিয়অন মুসলমানস্’ গ্রন্থে মিঃ হান্টার ইংরেজদের তাবেদার হয়েও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে,
“গাঙ্গের ব-দ্বীপ এলাকার ধর্মান্ধ মুসলমানরা নিজেদের ওয়াহাবী না বলে ফরায়েজী অর্থাৎ ইসলাম ধর্মের অনাবশ্যকীয় আচারানুষ্ঠানাদি বর্জন হিসেবে পরিচিত করে।... কলকাতার পূর্ব দিকের জেলাসমূহে এদের সংখ্যা বিপুলভাবে বৃদ্ধি পায়। ১৮৪৩ সালে এই সম্প্রদায়টি এতদূর বিপজ্জনক হয়ে ওঠে যে, তাদের সম্পর্কে তদন্তের জন্যে সরকারকে বিশেষ তথ্যানুসন্ধান কমিশন নিয়োগ করতে হয়। বাংলার পুলিশ প্রধান কর্তৃক প্রদত্ব রিপোর্টে বলা হয় যে, মাত্র একজন প্রচারক [হাজী শরীয়তুল্লাহ] প্রায় আশি হাজার অনুগামীর এক বিরাট দল গড়ে তুলেছে এবং তারা প্রত্যেকের ব্যক্তিগত স্বার্থেকে গোটা সম্প্রদায়ের স্বার্থ বলে বিবেচনা করে থাকে।”..
‘দি ইন্ডিয়ান মুসলানস্’ গ্রন্থে হান্টার আরো বলেন:
“সারা ভারতে তাদের প্রতিনিধি পাঠিয়ে ইতিহাসের এক বৃহত্তম ধর্মীয় পুনরুত্থান সাধিত করল তারা। তাঁদের অসংখ্য ছোট ছোট মিশনারী দল ছিল। দক্ষ সংগঠনের মাধ্যমে তারা মুরীদগণের তাকিদে যেখানে প্রয়োজন সেখানেই আস্তানা স্থাপন করতে পারত।... প্রত্যেক জেলাতেই একজন করে প্রচারক নিযুক্ত হয়। ভ্রাম্যমান মিশনারীরা মাঝে মাঝে এই সকল জেলা সফর কালে সেখানকার স্থায়ী প্রচারকদের উদ্যমকে জাগ্রত রাখতে থাকে। এইসব প্রচারকদের অশুভ প্রভাব ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল।.. এরা এমন ধর্মান্ধদের তহবিলে দান করেছিল... দলের পর দল সংগ্রহ করে ধর্মান্ধ শিবিরে পাঠিয়ে দেয়া হচ্ছিল। দেশের সর্বত্র মুসলমান জনসাধারণের মধ্যেতারা গভীর আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল... অজস্র রাজদ্রোহমূলক সাহিত্য, পাটনায় অবস্থিত কেন্দ্রীয় প্রচার কেন্দ্র এবং সারা বাংলার আনাচে কানাচে প্রচারকদের আনাগোনা ছাড়াও জনগণের মধ্যে রাজদ্রোহমূলক কাজে উৎসাহ সৃষ্টির জন্যে ওয়াহাবীরা [?] একটু চতুরথ সংগঠন গড়ে তুলেছে।... এইভঅবে পল্লী বাংলার বিভিন্ন স্থানে এক ধরনের বিদ্রোহী কলোনী গড়ে উঠেছে।... অর্থ সংগ্রহ ব্যবস্থাটা সহজ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল। গ্রামগুলোকে বিভিন্ন আর্থিক এলাকায় বিভক্ত করে প্রত্যেক এলাকার জন্যে একজন করে প্রধান ট্যাক্স আদায়কারী নিয়োগ করা হয়। যে গ্রামের জনসংখ্যা খুব বেশী সেখানে একাধিক আদায়কারী নিয়োগ করা হয় এবং তার মধ্যে একজন মৌলবী থাকতেন যিনি সমাজে ইমামতি করতেন.... একজন জেনারেল ম্যানেজার রাখা হয় যিনি মুসলমানদের দুনিয়াবী কাজের তদারক করতেন। এছাড়াও একজন অফিসার থাকতেন, তার কাজ ছিল বিপদজনক চিঠি-পত্র বিলি বন্টন ও রাজদ্রোহমূলক খবরাখবর আদান প্রদান করা।..”
হান্টর তার লেখায় ‘ওহাবী’ বলে যে সংগঠনের কথা বলেছেন আসলে তা আদৌ সঠিক নয়।
এটা ছিলো সম্পূর্ণ মিথ্যাচার।
‘ওহাবী’ বলতে পৃথিবীতে কোনো সংগঠনের অস্তিত্ব ছিল না।’
‘ওয়াহাবী’ বা ‘ওহাবী’ পরিভাষাটি ইউরোপীয়দের কল্পনারাজ্যের সৃষ্টি এবং ইসলামী আন্দোলনের জন্যে একটি গালি মাত্র।
সাইয়েদ আহমদ বেরেলভীর ‘জিহাদী আন্দোলনকে’ উপহাস করার জন্যে তারা তাদেরকে ‘ওহাবী’ বলে আখ্যায়িত করেছেন।
এটা ছিলো তাদের ঘৃণ্য এক পরিভাষা।
যেটা এখনো কাম্য ছিলো না।
প্রকৃত অর্থে ‘ওহাবী’ কথাটি সম্পূর্ণ সত্যের খেলাফ এবং ইসলাম বিরোধী। তাদের শত ষড়যন্ত্র আর অপপ্রচরের মধ্যেও ইংরেজের রিুদ্ধে এ সময় বিরামহীন সংগ্রাম চলছিলো।
ইংরেজরা তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করে চেয়েছিলো মুসলমানদের সংগ্রামকে প্রতিহত করতে।
কিন্তু তারা তা পারেনি।
পারেনি শত চেষ্টা করেও এই সংগ্রামকে দমাতে।
এ প্রসঙ্গে হান্টারের একটি উদ্ধৃতি এখানে উল্লেখযোগ্য। তিনি লেখেন:
“আমাদের সীমান্ত অঞ্চলে ১৮৩১ খৃস্টাব্দ থেকে শুরু করে ১৮৬৮ খৃস্টাব্দ তাদের বিরুদ্ধে আমাদের সর্বশেষ অভিযান পর্যন্ত ইতিহাস আলোচনা করলাম। ওহাবীরেদ [?] যুদ্ধাত্মক তৎপরতা ভারতের সর্বত্র যে বিস্তার লাভ করেছিল তার ইতিহাস আলোচনা করতে গেলে এই গ্রন্থের কলেবর বিরাট আকার ধারণ করবে... ধর্মান্ধদের দ্বারা সীমান্তে বিরামহীন অশান্তি বিরাজমান রাখা ছাড়াও তিনবার বৃহদাকার ঐক্যজোট সংঘটিত হয়েছে এবং প্রত্যেক বারই বৃটিশ ভারতকে একেকটি যুদ্ধের মাধ্যমে তার মুকাবিলা করতে হয়েছে।... কিন্তু এদের নির্মূল করার জন্যে আমাদে সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।... নিজেদের অবস্থা শেষ পর্যন্ত যে ভেঙ্গে পড়েছে তার নিদর্শন তাদের নিজেদের অবস্থা থেকেই বুঝা যাচ্ছে। তাদের প্রধান নেতারা ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার হয়েছে এবং অবশিষ্টরাও বুঝতে পেরেছে যে সক্রিয় হলে তাদেরও একই পরিণামের সম্মুখীন হতে হবে। কিন্তু সীমান্তের সশস্ত্র বিরাট ধর্মীয় মহা সম্মিলন রূপ গ্রহণ করবে। আজ সকালেই [১৪ই জুন, ১৮৭১] আমি এই পরিচ্ছেদ রচনার কাজ শেষ করার সময় জানতে পারলাম যে, ব্লাক মাউন্টেনের উপর বিদ্রোহী শিবির থেকে আরেকটি আক্রমণ পরিচালিত হয়েছে।”
তখনকার আন্দোলন সম্পর্কে হান্টারের আর একটি বিবেচনা:
“বাংলার মুসলমানরা আবার বিচিত্র রূপ ধারণ করেছে, গ্রাম পড়িয়েছে, আমাদের প্রজাদের হত্যা করেছে এবং আমাদের সীমান্তের ওপরে মাসের পর মাস ধরে গড়ে ওঠা শত্রু-বসতির লোক নিয়মিতভাবে সংগ্রহ করা হয়েছে বাংলাদেশের অভন্তরে থেকে। বিভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত রাজনৈতিক মোকাদ্দমার বিচার থেকে একথাই প্রমাণিত হয় যে, আমাদের প্রদেশসমূহের সর্বত্র বিস্তারিত হয়েছে এক ষড়যন্ত্রের জাল। পাঞ্জাবের উত্তরে অবস্থিত জনহীন পর্বতরাজির সঙ্গে উষ্ণ মণ্ডলীয় গঙ্গা অববাহিকার জলাভূমি অঞ্চলের [বাংলার] যোগসূ্ত্র স্থাপিত হয়েছে রাজদ্রোহীদের নিরবিচ্ছিন্ন সমাবেশের মাধ্যমে। সুসংগঠিত প্রচেষ্টায় তারা ব-দ্বীপ অঞ্চল [বাংলা] থেকেঅর্থ ও লোক সংগ্রহ করে এবং দুই হাজার মাইল দূরে অবস্থিত বিদ্রোহী শিবিরে তা চালান করে দেয়।... বাংলার এমন কোন জনপদ ছিল না যেখানকার মুসলমানদের মধ্যে সৈয়দ সাহেবের সংস্কারের বাণী ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেনি। প্রতিটি ধার্মিক পরিবারের যুবকরা সীমান্তে গিয়ে জিহাদ করার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করত। বৃটিশ সরকারের গোয়েন্দার চোখ ফাঁকি দিয়ে একদিন তারা হঠাৎ করে সীমান্তের মুজাহিদ কাফেলায় যোগ দেবার উদ্দেশ্যে বের হয়ে পড়ত। জমির খাজনা পরিশোধ করতে অসমর্থ কৃষকরাও জিহাদের জন্য নিয়মিত অর্থ প্রদান করতে কুণ্ঠিত হতো না।”
হান্টারের লেখায় এই ভাবেই বিষেদগারের পাশাপাশি অনেক সত্যও বেরিয়ে আসে।
কয়েকটি বিবেচনা
ফরায়েজী আন্দোলনকে বিশ্লেষণ করে প্রাজ্ঞজনেরা কয়েকটি বিবেচনায় উপনীত হয়েছেন। বিবেচনায় উপনীত হয়েছেন। বিবেচনাগুলো:
১. মহান মর্দে মুজাহিদ হাজী শরীয়তুল্লাহর গড়ে তোলা এই আন্দোলন ছিলো পূর্ব ভারতের প্রথম একমাত্র ইসলামী আন্দোলন।
যার লক্ষ্য ছিলো বিদেশীদের হাত থেকে মুসলমানদের স্বাধীন ও মুক্ত করা এবং সংগঠিত করা।
২. হাজী শরীয়তুল্লাহর এই আন্দোলন কোনো সাময়িক আবেগতাড়িত ব্যাপার ছিলো না, বরং এটি ছিলো একটি প্রাণবন্ত আন্দোলন।
আর এই কারণেই এতো দীর্ঘ সময় ধরে আমরা এর প্রাণস্পন্দন দেখতে পাই।
৩. প্রথম দিকে এই আন্দোলন ছিলো ইসলামী সংস্কারমূলক। কারণ তখনকার কর্মসূচী ছলো আকীদা বিশ্বাসের সংশোধন এবং বিদয়াতমূলক আচার অনুষ্ঠান উচ্ছেদ।
কিন্তু পরবর্তীকালে ধীরে ধীরে সামাজিক ও রাজনৈতিক দিকগুলো ও এর সাথে যুক্ত হয়ে যায়।
এমনকি এক পর্যায়ে সময়ের প্রয়োজনে লাঠিয়াল বাহিনীরূপে সামরিক শক্তিও গড়ে তোলা হয়।
৪. ফরায়েজী আন্দোলনের আকীদা বিশ্বাসের কথা বলতে গেলে বলতে হয়, এই বিপ্লবের প্রতি ঐতিহাসিকরা যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করেনন। বরং বিকৃতভাবে তারা সেটা উপস্থিাপিত হয়েছে।
কারণ তাদের লেখায় আকীদা বিশ্বাসের তুলনায় এই আন্দোলনের সামাজিক কাজকর্ম বেশি মাত্রায় ফুটে উঠেছে। অথচ আকীদা বিশ্বাসের সংশোধন এবং ধ্যান ধারণা পরিশুদ্ধির ক্ষেত্রেও এই আন্দোলন ব্যাপক তথা প্রধান ভূমিকা পালন করেছে।
৫. এই আন্দোলন ছিলো ইসলামী আদর্শভিত্তিক স্বাধীনতা আন্দোলন।
এতে যেমন ঈমান আকীদার পরিশুদ্ধির প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছিলো তেমনি সাধারণ মানুষের অধিকার আদায়েরও বলিষ্ঠ প্রতিশ্রুতি এতে ছিলো। এর ছায়াতলে সংঘবদ্ধ হতে অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলো অসংখ্য কৃষক। তাই এ আন্দোলনকে কৃষক আন্দোলনও বলা যায়।
প্রতিপক্ষের শ্যৈন দৃষ্টি
হিন্দুরা কখনই মুসলমানদেরকে সুনজরে দেখেনি।
তারা মুসলমানদের ইংরেজ-বিরোধী আন্দোলনকেও সহ্য করতে পারতো না। তারা ইংরেজদেরকে তুষ্ট করার জন্যে সর্বদা তৎপর থাকতো।
আর মুসলমানদের বিরোধিতা করাই ছিলো তাদের মজ্জাগত স্বভাব।
আঠারো শো সাতান্ন সালে যখন স্বাধীনতা সংগ্রামী ইংরেজের কামানের গোলায় জীবন দিচ্ছিলো, তখন হিন্দু পত্রিকায় লেখা হয়েছিলো:
“আমরা পরমেশ্বরের সমীপে সর্বদা প্রার্থনা করি, পুরুষানুক্রমে যেন ইংরেজাধিকার থাকিতে পারি। ভারত ভূমি কত পুণ্য করিয়াছিলেন এই কারণে ইংরেজ স্বামী পাইয়াছেন, মৃত্যুকাল পর্যন্ত যেন ইংরেজ ভূপালদিগের মুখের পান হইয়া পরম সুখে কাল যাপন করেন।” [সংবাদ ভাস্কর: ২০শে জুন, ১৮৫৭]
এই ছিলো হিন্দুদের মনোভাব!
স্বাধীনতা সংগ্রামী মুসলমানদেরকে হিন্দু পত্রিকাগুলো কোন দৃষ্টিতে দেখতো এবং বন্দী স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতি কি ধরনের নিষ্ঠুর মনোভাব প্রকাশ করতো তা নিচের আর একটি উদ্ধৃতি থেকেই সহজে অনুমান করা যায়।
আঠারো শো সাতান্ন সালের আঠারো ও বিশে জুনের ‘সংবাদ ভাস্কর’-এ আবারও লেখা হয়:
“আগ্রা, দিল্লী, কানপুর, অযোধ্যা, লাহোর প্রদেশীয় ভাস্কর পাঠক মহাশয়েরা এই বিষয়ে মনোযোগ করিবেন এবং পাঠ করিয়া বিদ্রোহীদের আড্ডায় ইহা রাষ্ট্র করিবেন এবং পাঠ করিয়া বিদ্রোহীদের আড্ডায় আড্ডায় ইহা রাষ্ট্র করিয়া দিবেন, সিপাহীরা জানুক বৃটিশ গভর্নমেন্ট সিপাহী ধরা আরম্ভ করিয়াছেন, আর বিদ্রোহী সকল শোন্ শোন্, তোদের সর্বনাশ উপস্থিত হইল, যদি কল্যাণ চাহিস তবে এখনও বৃটিশ পদান হইয়া প্রার্থনা কর-ক্ষমা করুন।.. গত বুধবার বেলা দুই প্রহর, ঘন্টাকালে সৈন্য পরিপূর্ণ এক জাহাজ উত্তর দিক হইতে আসিয়িা কলিকাতা দুর্গের দক্ষিণাংশে লাগিল। সে সময় উক্ত জাহাজ অতি সুদৃশ্য দৃষ্ট হইল, গোরা সৈন্যরা পাঁচশ’ সিপাহীকে হাতে হাতকড়ী পায়ে পবেড়ী দিয়া লইয়া আসিয়াছে, গভর্ণমেন্ট সিপাহীদিগের প্রতি যে প্রকার ক্রোধ করিয়া রহিয়াছেন, তাহাতে বলিদান দিনে ইহাই জ্ঞানগ্রাহ্য হইতেছে। কালিঘাটে বহুকাল নরবলি হয় নাই। আমাদিগের রাজেশ্বর যদি হিন্দু হিইতেন, তবে এই সকল নরবলি দ্বারা জগদম্বার তৃপ্তি করিতেন।”
অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় বটে!
তবুও এটাই সত্য যে, হিন্দুরা কখনই ইসলামী আন্দোলন ও স্বাধীনতা- সংগ্রামকে সুনজরে দেখেনি।
বরং এর তীব্র বিরোধিকা করেছে প্রতিটি পদক্ষেপে।
আশার কথা, তবুও থেমে থাকেনি হাজী শরীয়তুল্লাহসহ মর্দে মুজাহিদদের সংগ্রাম। দুর্বার আন্দোলনের ক্রমধারা!
একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য
ভারতীয় রাজনীতি পর্যালোচনা করতে গিয়ে স্যার উইলিয়াম হান্টার আঠারো শো একাত্তর সালে লেখেন,
“এতে কোনো সন্দেহ নেই যে ভারত গভর্নমেন্ট যদি পূর্ব থেকেই ষড়যন্ত্র আইনের ৩ নং ধারা অনুযায়ী ভারতের আলেমদের কঠোর হস্তে শাসন করতো, তাহলে ভারত গভর্নমেন্টকে মুজাহিদ আলেমদের আক্রমণের ফলে এত দুঃখ ভোগ করতে হতো না। কতিপয় আলেমকে গ্রেফতার হতো না এবং লক্ষ লক্ষ পাউন্ড বেঁচে যেত। এমন কি উক্ত লড়াই-এর পরও যদি কঠোর হস্তে আলেমদেরকে দমন করা হতো তবে অন্ততপক্ষে ১৮৬৮ খৃস্টাব্দে কালাপাহাড় অভিযান হতে রক্ষা পাওয়ার আশা ছিল।”
উইলিয়াম হান্টর এখানে আলেমদের কঠোর হস্তে দমন না করায় দুঃখ ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছন!
কিন্তু প্রকৃত সত্য হলো, ইংরেজরা তাদের সাধ্যানুসারে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে এমন কোনো কঠোর পদক্ষেপ নিতে বাদ রাখেনি।
ফকির বিদ্রোহকে তারা কঠোর হাতেই দমন করেছিলো!
তিতুমীর ও হাজী শরীয়তুল্লাহর সংগ্রামকেও দমন করার জন্যে ইংরেজরা সকল প্রকার জুলুম নির্যাতন চালিয়েছিলো!
সংগ্রামরত মুসলমানদের প্রতি ইংরেজরা ছিলো বরাবরই কঠোর ও নির্মম!
সমগ্র ভারত বর্ষ বিস্তৃত সাইয়েদ আহমদ বেরেলভীর স্বাধীনতা সংগ্রামকেও শত রকম নির্যাতনের মাধ্যমে তারা প্রতিহত করার চেষ্টা করেছিলো।
ইংরেজদের শত বাধা এবং হিন্দুদের হাজার চেষ্টাতেও এ উপমহাদেশের সংগ্রামরত বীর মুজাহিদদের আন্দোলন কখনো থেমে থাকেনি।তাদের রক্ত-চক্ষুকে উপেক্ষা করে সর্বদা এগিয়ে গেছেন সকল সাহসী সৈনিক! এই সাহসী সৈনিকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন হাজী হাজী শরীয়তুল্লাহ।
আমৃত্যু তিনি লড়ে গেছেন একজন প্রকৃত সৈনিকের মতো!
লড়ে গেছেন সত্যের পক্ষে এবং মিথ্যার বিরুদ্ধে।
ইতিহাসের পুনর্পাঠ
২৮শে জানুয়ারী ১৯৯৯ সাল।
এই দিনে বাংলাদেশের একটি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ করলো হাজী শরীয়তুল্লাহর ওপর একটি সংখ্যা।
যেটা ছিলো ব্যতিক্রম এবং অভিনন্দনযোগ্য।
মূল শিরোনামছিলো- “বাংলাদেশের জাতীয় জাগরণের অন্যতম পথিকৃত ঐতিহাসিক ফরায়েজী আন্দোলনের স্থপতি মহান স্বাধীনতা সংগ্রামী হাজী শরীয়তুল্লাহর ১৫৯তম মৃত্যু বার্ষিকী বিশেষ সংখ্যা।”
এই বিশেষ সংখ্যায় দু’টি গুরুত্বপূর্ণ লেখা প্রকাশিত হয়।
প্রথমটির লেখক অধ্যাপক আবদুল গফুর। শিরোনাম- “হাজী শরীয়তুল্লাহ এবং বৃটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রাম।”
দ্বিতীয়টি লেখক মুন্শী আবদুল মান্নান। তাঁর শিরোনাম ছিল- “ফরায়েজী আন্দোলন : তার পটভূমি ও লক্ষ্য।”
খুবই প্রসঙ্গিক হওয়ায় গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে প্রবন্ধ দু’টির অংশবিশেষ এখানে সংযুক্ত করা হলো।
অধ্যাপক আবদুল গফুর তাঁর প্রবন্ধে উল্লেখ করেন:
“আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে হাজী শরীয়তুল্লাহ লাল হরফে লিখে রাখার মত একটি নাম।
হাজী শরীয়তুল্লাহর নামের সাথে জড়িয়ে আছে ফরায়েজী আন্দোলন নারেম একটি সংস্কার আন্দোলনের ইতিহাস।
ফরায়েজী আন্দোলণ পাঠকদের কাছে পরিচিত হয়ে আছে একটি ধর্মীয়, সামাজিক সংস্কার আন্দোলন হিসেবে।
তার প্রতিষ্ঠাতা স্বাধীনতা সংগ্রামে ভূমিকা রাখেন কি করে, এ প্রশ্ন উত্থাপিত হওয়া খুবই স্বাভাবিক।
এ প্রশ্নের জওয়াব পেতে হলে আমাদের ফরায়েজী আন্দোলনের প্রকৃতি ও পটভূমির দিকে সন্ধানী দৃষ্টিতে তাকাতে হবে।
হাজী শরীয়তুল্লাহকে আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ হিসেবে মেনে নিলেও তাঁর হাতে যে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম সূচনা হয়নি, এটাও এক ঐতিহাসিক সত্য।
অবিশ্বাস্য হলেও সত্য এই যে, ১৭৫৭ সালের পলাশীতে আমাদের স্বাধীনতা হারাবার মাত্র আট বছরের মাথায় ১৭৬৪ সালে আমাদের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার সংগ্রামের সূচনা করেন এমন এক ব্যক্তি, যিনি পলাশী ষড়যন্ত্রেরও অন্যতম সহযোগী ছিলেন।
তিনি মীর জাফর আলী খাঁর জামাতা মীর কাসিম আলী।
ইংরেজরা মীর জাফরকে সরিয়ে মীর কাসিমকে নবাব করার অল্পদিন পরই তিনি ইংরেজ আধিপত্যের বিরুদ্ধে প্রথম সংঘাতে, পরে সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত হন।
কিন্তু ধনুক থেকে একবার তীর ছোঁড়া হয়ে গেলে তা যেমন ফিরে আসে না, মীর কাসিমের এ স্বাধীনতা সংগ্রামও তেমনি স্বাভবিক কারণেই ব্যর্থ হয় এবং স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার সংগ্রাম শুরুর দায়ে তাকে করুণ মৃত্যুবরণ করতে হয়।
মীর কাসিমের প্রায় সমসাময়িক কালেই মজু শাহের নেতৃত্বে উত্তরবঙ্গে আরেকটি স্বাধীনতা সংগ্রাম সূচিত হতে দেখা যায়।
ইতিহাসে এটি ফকির আন্দোলন রূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।
১৭৬৩ সালে ফকির বাহিনী ঢাকায় ইস্ট কোম্পানীর কুঠির ওপর প্রথম আক্রমণ পরিচালনা করেন।
ইংরেজদের হাতে পর্যুদস্ত রণক্লান্ত মীর কাসিম ১৭৭৭ সালে অসহায়ভাবে ইন্তেকাল করেন।
কিন্তু ফকির মজনু শাহের সূচিত ফকির আন্দোলন ১৭৮৭ সাল তাঁর মৃত্যুর পরও বহুদিন পর্যন্ত জারি ছিল।
মজনু শাহের মৃত্যুর পর তাঁর ভাই মুসা শাহ ফকির আন্দোলনের নেতা হন। ১৭৯১ পর্যন্ত মুসা শাহ ও তাঁর অন্যতম সহযোগী চেরাগ আলী যে রংপুর ও ময়মনসিংহ এলকায় সক্রিয় ছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায়।
তবে ফকিররা প্রধানত ইংরেজদের এবং তাদের আশীর্বাদপুষ্ট জমিদারদের ওপর আচমকা আক্রমণ চালিয়ে তাদের জানমালের ক্ষয়ক্ষতি সাধনের বাইরে স্বাধীনতা আন্দোলনে কোনো সুপরিকল্পিত সাংগঠনিক কর্মসূচী নিয়ে অগ্রসর হননি বলে এ আন্দোলনকেও আঠার শতকের শেষাশেষি স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করে।
স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে ফরায়েজী আন্দোলনের গুরুত্ব অনুধাবন করতে হলে আমাদের অবশ্য এর পটভূমি এবং এর প্রতিষ্ঠানের জীবন, কর্ম ও চিন্তাধারাকে সূক্ষ্মভাবে পর্যালোচনা করতে হবে।...
হাজী শরীয়তুল্লাহ মক্কায় যান ১৭৯৯সালে এবং সেখানে একটানা ২০ বছর কাটিয়ে ১৮১৮ সালে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন।
এই দীর্ঘ সময়কাল তিনি কাটান ধর্মীয় অধ্যয়ন ও সাধনায়।
আরব দেশে তখন মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওহাব [১৮০৩-৯২] পরিচালত ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের জোয়ার চলছে।
তিনি এ আন্দোলনের সংস্পর্শে এসে মুসলিম সমাজে শিরক, বিদয়াত প্রভৃতি অবাঞ্ছিত ইসলাম বিরোধী কুসংস্কারের অনুপ্রবেশ সম্পর্কে সচেতনতা লাভ করলেও ঐ আন্দোলনের সাথে যোগ দেননি।
কারণ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওহাবের সূচিত আন্দোলনের মাযহাব বিরোধিতা তাঁর মনঃপুত হয়নি।
বাংলাদেশের অধিকাংশ মুসলমান মাযহাব হানাফী মাযহাব বাদ দিয়ে হাম্বলী মাযহাবে দাখিল হওয়ার কোন জরুরত তিনি অনুভব করেননি।
তিনি মক্কা শরীফেও একাধিক হানাফী আলেম ও বুজুর্গের কাছে ইসলাম সম্পর্কে উচ্চতর শিক্ষা লাভ করেন।
দুই বছর তিনি কায়রোর আল-আজহারে শিক্ষা লাভকরেন।
আরব দেশে দীর্ঘকাল অবস্থান এবং ধর্ম সম্পর্কে গভীর অধ্যয়ন ও গবেষণার পর তিনি যে স্বপ্ন স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন পরাধীন দেশবাসীর করুণ অবস্থা দেখে তাঁর সে স্বপ্ন অনেকাংশেই উবে যেতে চাইলো। হাজী শরীয়তুল্লাহ দেখলেন, তাঁর দেশবাসী যেন শুধু রাজনেতিক ভাবেই গোলামীর শিকরে বাঁধা পড়িন, ধর্মীয়, সামাজিক,সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়েও স্বাধীন স্বতন্ত্র সত্তা হারিয়ে বসে আছে।
স্বাধীনতা হারানোর ছয় দশকের মধ্যেই তাদের এ করুণ অবস্থা দেখে তাঁর মন বেদনার্ত হয়ে উঠলো।
তিনি দেখলেন পৃথিবীতে যে ইসলাম এসেছিল মানুষকে জীবনের সর্বপর্যায়ে স্বাধীনভাবে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর শিক্ষা দিতে, সেই ইসলামের অনুসারী হয়েও তাঁর স্বদেশবাসী অধঃপতনের নিম্নতম পর্যায়ে নেমে গেছ।
তাদের চোখের সামনে ইসলামের সে বিপ্লবী রূপের সামান্যতম ছবিও আর উপস্থিত নেই।
ইসলামের কালেমা এসেছিল ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’... এক আল্লাহ ছাড়া মানুষের আর কোনো প্রভু নেই- এই বিপ্লবী আদর্শ শিক্ষা দিতে।
অথচ তার স্বজাতির মধ্যে চলছে অসংখ্য নকল খোদার দাপট আর প্রবুত্ব।
ইসলাম এসেছিল দুনিয়ায় তৌহিদের আদর্শ এক আল্লাহর বন্দেগী বা আনুগত্য শিক্ষা দিতে।
অথচ শরীয়তুল্লাহ দেখলেন, তাঁর সমাজের লোকেরা এক আল্লাহর ইবাদাতের স্থলে পীর পূজা, কবর পূজা, ইংরেজ পূজা, জমিদার পূজা, মহাজন পূজার মাধ্যমে অসংখ্য নকল খোদার পূজায় লিপ্ত রয়েছে।
মুসলিম শাসনামলেও যে সমাজের সর্বস্তরে ইসলামের বিধান পুরোমাত্রায় চালু ছিল, তা হয়ত নয়।
তবুও মানুষের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা তখন অনেকটাই সমুন্নত ছিল।
ফলে হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সকলের নিজ নিজ ধর্মীয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক জীবনে পর্যাপ্ত স্বাধীনতা ও সমৃদ্ধি ছিল।
সোনার বাংলার সেদিনের সেই সমৃদ্ধি সম্পদের লোভেই সাত সমুদ্রের ওপর থেকে এসে বণিকবেশী ইংরেজরা ষড়যন্ত্র পাকিয়েছিল এদেশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে।
পলাশীর ষড়যন্ত্রে ইংরেজদের সাথে হাত মিলিয়ে জগৎশেঠ, রাজবল্লভ, রায়দুর্ভল ও উমিচাঁদেরা এদেশে মুসলিম শাসন উৎকাতে সাহায্য করার পারিতোষিক ঠিকই পেয়েছিল সুদে-আসলে।
পলাশী যুদ্ধের আট বছরের মধেই আশি হাজার মুসলমান সেনাবাহনিী থেকে বরখাস্ত হয়।
একে একে সমস্ত মুসলমান আমীর-ওমরাহকে সরকারী পদ থেকে অপসারিত করে সেখানে ইংরেজভুক্ত হিন্দুদের নিয়োগ করা হয়।
বেছে বেছে মুসলমান আয়মদার, জায়গীরদার উৎখাত করে সেখানে ইংরেজ খয়ের খাঁ হিন্দুদের বসানো হয়।
মুসলিম শাসনামলে জমিদাররা কখনও জমির মালিক ছিল না, জমির প্রকৃত মালিক ছিল কৃষকরা, জমিদাররা শুধু নির্দিষ্ট মেয়াদে রাজস্ব আদায় করত। ১৭৯৩ সালে সে ব্যবস্থা রহিত করে কৃষকদের মাথার ওপরে জমিদারদের জমির চিরস্থায়ী মালিক করে বসিয়ে দেয়া হল।
বলাবাহুল্য এই নতুন জমিদারদের প্রায় সবাই ছিল হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত।
এরা কৃষকদের ওপর করের পর কর বসিয়ে তাদের জীবনকে অতিষ্ঠ করে তুললো।
জমিদারের ছেলে মেয়েদের বিবাহ ও নানা পার্বণ উপলক্ষে প্রজাদের কাছ থেকে কর আদায় করা হতে লাগলো।
মুসলমান প্রজাদের ওপর অতিরিক্ত থাকত দাড়ির ট্যাক্স এবং আজান ও গরু কুরবানির ওপর নিষেধাজ্ঞার মত জঘন্য অত্যাচার।
একদিকে জমিদারদের জুলুম, নির্যাতন, অন্যদিকে নব্য ধনিক হিন্দু মহাজনদের কুমিদ ব্যবসা- দুইযে মিলে গ্রামের সাধারণ মানুষ, বিশেষকরে মুসলমানদের জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠেছিল।
মুসলিম শাসনামলের যে মসলিন বস্ত্র-শিল্প একদা সারা বিশ্বে খ্যাতি অর্জন করেছিল, তাকে ধ্বংস করে দেয়ার জন্য মসলিন শিল্পীদের হাতের আঙ্গুল কেটে ফেলার মত নৃশংসতা প্রদর্শনেও ইংরেজদের দ্বিধা হয়নি।
পলাশী বিপর্যয়ের পর মুর্শিদাবাদসহ বাংলার সম্পদ লুন্ঠনের মাধ্যমে ইংল্যান্ড নতুন করে সমৃদ্ধি নির্মাণের পালা শুরু হয়, যার ফলে সেদেশে শিল্প বিপ্লব সম্ভব হয়।
ইংল্যান্ডের বস্ত্র-শিল্পের জন্য জায়গা করে দিতে এদেশের উন্নত বস্ত্র-শিল্পই শুধু ধ্বংস করা হল না, কৃষকদের অর্থনৈতিক মেরুদন্ড অর্থকারী ফসলের স্থলে নীলচাষেকৃষকদের বাধ্য করা হতে লাগলো।
বিদেশী শাসক এবং তাদের এতদ্দেশীয় দালালদের মিলিত ষড়যন্ত্রের ফলে- যে দেশে মুসলিম শাসনের ৫০০ বছরে কোনো দুর্ভিক্ষহয়নি, পলাশী বিপর্যয়ের মাত্র দুই দশকের মধ্যেই ছিয়াত্তরের দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। এই ভয়াবহ দুর্ভিক্ষে কুকুর-বিড়ালের মত প্রাণ হারালো এদেশের লাখ কোটি বনি আদম।
একদিকে এদেশের জনগণের করুণ অবস্থা, অন্যদিকে শিক্ষা-দীক্ষা, অর্থনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, ধর্ম-সংস্কৃতি সকল দিকে মুসলমানদের অসহায়তা পর্যায়ে।
মুসলমানদের ভুলিয়ে দেয়া হয়েছিল তাদের সুমহান সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের কথা।
তারা হিন্দুদের অনুকরণে বসন্ত রোগে শীতলা দেবীর পূজা, সর্প দংশনে মজমা পূজা প্রভৃতিতে লিপ্ত হতে লাগলো বিনা দ্বিধায়।
অন্যান্য পূজায় সরাসরি অংশ না নিলেও পূজা-পার্বনে চাঁদা দেয়া ও নৈবেদ্য ভক্ষণে অংশগ্রহণ নিজেদের দায়িত্বের অন্তর্গত করে নিয়েছিল।
তারা শিশুর নাম রাখতে লাগল হিন্দুদের অনুকরণে।
হজ্ব, যাকাত তো আগেই ভুলেছিল, নামায-রোযাও আস্তে আস্তে ভুলে যেতে লাগল।
একদিকে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এসব বিচ্যুতি, অন্যদিকে ইসলামের সামাজিক সাম্য, ভ্রাতৃত্বের কথা ভুলে গিয়ে হিন্দুদের কুলীণ-অকুলীন, বড়জাত-ছোটজাতের ভেদ বৈষম্যের অনুকরণে বিভক্ত করে ফেললো।
শ্রেণীতে নিজেদের বিভক্ত করে ফেললো। রাসূল [সা] যেখানে বলেছেন, পরিশ্রমের মাধ্যমে জীবিকা অর্জনকারী আল্লাহর বন্ধু, সেখানে কৃষকদের ‘চাষা’, তাঁতীদের ‘জোলা’ বলে তাদের নীচু জাতের মানুষ ভাবতে শুরু করলো মুসলমানরা।
ইসলামেযে বলা হয়েছিল- বর্ণ, রক্ত, বংশ, গোত্র বা পেশার ভিত্তিতে নয়,একমাত্র ধর্মনিষ্ঠা তথা তাকওয়ার ভিত্তিতেইইসলামে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব নির্ধারত হয়, সেই শিক্ষা এভাবেই মুসলমানরা ভুলে গিয়েছিল।
হাজী শরীয়তুল্লাহ শুধু ইসলাম সম্পর্কে অধ্যয়নই করেননি, স্বদেশে ও স্বজাতির এই দুঃজনক অবস্থার কারণে নিয়েও যথেষ্ট পড়াশুনা ও চিন্তাভাবনা করেন গভীরভাবে।
স্বদেশে ও স্বজাতির এই চরম দুরবস্থার প্রধান কারণ যে পরাধীনতার প্রভাব, এ সম্বন্ধে তাঁর মনে কোনই সন্দেহ ছিল না।
কিন্তু স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের জন্য মুসলমানদের যে প্রস্তুতি প্রয়োজন, সচেতনতা অপরিহার্য তার কোনো লক্ষণই মুসলিম সমাজে তিনি দেখতে পেলেন না।
এমনকি ইসলামের অনুসারী কোনো জনগোষ্ঠী যে কোনো পর্যায়েই আল্লাহ ছাড়া কারো গোলামীকে মেনে নিতে পারে না- সেই চেতনা, সেই অনুভূতি কোথায়?
শুধু স্বাধীনতার কথা বললেই তো আর হবে না!
মীর কাসেম ও মজনু শাহদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ব্যরথতার ইতিহাস হাজী শরীয়তুল্লাহর সামনেছিল।
তাই জাতির মন-মানসিকতার ক্ষেত্রে স্বাধীনতার ভিত রচনার লক্ষ্যে তাদের মধ্যে প্রথমে একটি স্বাধীনতাকামী জাতি হিসেবে কর্বত্য সচেতনতা সৃস্টির সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য নিয়ে তিনি কাজে নামলেন।
হাজী শরীয়তুল্লাহ জাতির স্বাধীনতাকে চূড়ান্ত লক্ষ্য হিসেবে রেখে যে সংস্কার আন্দোলনের সূত্রপাত করেন তার নাম- ‘ফরায়েজী আন্দোলন’।... সেদিনের মুসলিম সমাজকি আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে, কি সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক- সকল ক্ষেত্রেই তার আদর্শ হারিয়ে ফেলেছিল।
হারিয়ে ফেলেছিল একটি পূর্ণাঙ্গ আদর্শ ইসলামের আলোকে তার অবশ্য পালনীয় দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতনতা।
এই দায়িত্ব তথা অপরিহার্য কর্তব্য সচেতনতা জাতির মধ্যে সৃষ্টি করতেই তিনি তাঁর আন্দোলনের নাম ‘ফরায়েজী আন্দোলন।’
এই আন্দোলনের মাধ্যমে মুসলমানদের মধ্যে তিনি ধর্মীয়, আধ্যাত্মিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কর্তব্য সচেতনতা সৃষ্টির আহ্বান জানান।
ইসলামে আধ্যাত্মিকতার যে উচ্চস্থান রয়েছে, তা মেনে নিয়েও শরীয়তুল্লাহ সমাজের এক শ্রেণীর ধর্ম ব্যবসায়ীর পীর-মুরিদী ব্যবসাকে নিরুৎসাহিত করার লক্ষ্যে ‘পীর’-‘মুরিদ’ শব্দ দু’টি পরিহার করে তার স্থানে আধ্যাত্মিক শিক্ষককে ‘ওস্তাদ’ ও অনুসারীকে ‘শাগরেদ’ বলে আখ্যায়িত করতে প্রয়াস পান এবং অতীতের ইহুদী নামাবাতের মত ধর্মগুরুদের প্রভু বলে পূজা করার প্রবণতার বিরুদ্ধে সকলকে সাবধান করে দেন।
ইসলামের সামাজিক ক্ষেত্রে সাম্য-ভ্রাতৃত্বের আদর্শের আলোকে হিন্দু কুলীন-অকুলীন প্রথার মত মুসলমান সমাজে আশরাফ-আতরাফ শ্রেণীভেদ সৃষ্টির বিরুদ্ধে তিনি সকলকে সতর্ক করে দেন।
যেহেতু ইসলামে শ্রমের মাধ্যমে জীবিকা অর্জনকারীর অতি উচ্চ মর্যাদা, তাই তাদেরকে চাষা, জোলা প্রভৃতি বলে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করার বিরুদ্ধে তিনি সকলকে হুঁশিয়ার করে দেন এবং সকল স্তরের মানুষের মধ্যে সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও শ্রমের মর্যাদা প্রভৃতি ইসলামী মূল্যবোধ প্রবর্তনের প্রয়াস পান।
মুসলমানদের মধ্যে সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মুসলমানদের মধ্যে যে আচার আচরণ ও অনৈসলামী কুসংস্কার অনুপ্রবেশ করেছিল, সেসব দূর করার জন্যে তিনি আকুল আহবান জানান।
ধর্মীয় আবশ্যিক কর্তব্যাদি যেমন- কালেমা, নামায, রোযা, হজ, যাকাত- এগুলো পালনের পাশাপাশি তিনি মুসলমানদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি এবং অন্যায়-অনাচার প্রতিরোধে তাদেরকে সংঘবদ্ধ করে তোলেন।
শিরক, বিদআত, অনৈসলামী কুসংস্কার ও বিজাতীয় অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে পরিচালিত আদর্শবাদী সংস্কার আন্দোলনে তিনি মুসলমানদের সংঘবদ্ধ করে তোলেন।
তাঁর আন্দোলন যদিও প্রত্যক্ষভাবে সীমাবদ্ধ ছিল ধর্মীয়, আধ্যাত্মিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে- তবুও পরোক্ষভাবে তিনি অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনেরও বুনিয়াদ গড়ে তোলেন।
যার ভিত্তিতে তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর সুযোগ্য পুত্র মুহাম্মদ মহসিন উদ্দিন ওরফে দুদু মিয়া গড়ে তোলেন বিপ্লবী রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক আন্দোলন। দুদু মিয়ার সেই আন্দোলনের ফলে একদিকে বৃটিশশাসকগোষ্ঠী, অপরদিকে তাদের আশীর্বাদপুষ্ট শোষক জমিদার গোষ্ঠীর ভিত্তিমূল পর্যন্ত প্রকম্পিত হয়ে ওঠে।
ফলে, ফরায়েজী আন্দোলনের সেই সিংহপুরুষকে বৃটিশরাজ প্রায় আমৃত্যু কারাগারে শৃংখলিত রাখতে বাধ্য হয়।
হাজী শরীয়তুল্লাহর চূড়ান্ত লক্ষ্য ছিল যে বৃটিশ শাসনের অবসান ঘটিয়ে দেশকে স্বাধীন করে তোলা, তার বড় প্রমাণ- পরাধীন দেশকে ‘দারুল হরব’ [ইসলাম বিরোধী রাষ্ট্র] ঘোষা করে স্বাধীনতা না আসা পর্যন্ত ঈদ ও জুমআর নামায স্থগিত রাখার পক্ষেতাঁর ঘোষণা। দেশের মুসলিম শাসক বা তার প্রতিনিধির উপস্থিতি এখানে অপরিহার্য।
এই দৃষ্টিতে তিনিএ রায় ঘোষণা করেন।
তিনি নিজে ঈদ বা জুমআর ভক্ত ছিলেন না, তা নয়।
স্বাধীনতা সংগ্রামের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিতেই তিনি এ ঘোষণা দিয়েছিলেন। জনগণের মধ্যে স্বাধীনতা সংগ্রামের মন-মানসিকতা সৃষ্টিতে তাঁর ঐতিহাসিক ভূমিকা কোনো মতেই অস্বীকার করা সম্ভব নয়।
হাজী শরীয়তুল্লাহর উত্তরসূরিগণ স্বাধীনতার লক্ষ্যে প্রবর্তিত তাঁর আন্দোলনকে নানা বাধা-বিপত্তির মধ্য দিয়েও যৌক্তিক পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যান।
শরীয়তুল্লাহর পুত্র মুহাম্মদ মহসিন উদ্দিন দুদু মিয়ার সময় ফরায়েজী আন্দোলন শক্তিশালী গণ-আন্দোলনে পরিণত হয়।
দুদু মিয়া তাঁর প্রভাবাধীন এলাকাকে কয়েকটি খণ্ডে বিভক্ত করেন এবং একেক অংশেরজন্য একেকজন খলীফা নিয়োগ করেন।
তার প্রভাবাধীন এলাকায় জনগণের মামলার শালিসের ব্যবস্থা তিনিই করতেন। কোনো মামলা-মোকদ্দমার জন্য ইংরেজদের আদালতে যাওয়ার তিনি নিষেধ করে দেনে।
এদেশে কৃষক আন্দোলনের ভিত্তি রচনা করে তিনি ঘোষণা দেন- জরি মালিক আল্লাহ। সুতরাং চাষীরা তাদের আয়ত্তাধীন জমির খাজনা সরকার বা জমিদারকে দেবে না।
এতে করে স্বাভাবিকভাবেই সরকার ও জমিদারদের সাথে তাঁর সংঘাত এবং সংঘাত থেকে সংঘর্ষ বেধে যায়।
এসব সংঘর্ষ-সংঘাতের শেষ পরিণতিতে সরকার তাঁকে দীর্ঘদিন কারারুদ্ধ করেরাখে।
দীর্ঘ কারা ভোগের ফলে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং কারাগার থেকে মুক্তি লাভের অল্পদিন পরেই তিনি ইন্তিকাল করেন।
দুদু মিয়ার মৃত্যুর পর তাঁর তিন পুত্র গাজী উদ্দিন হায়দার [১৮৬২-৬৪], আব্দুল গফুর ওরফে নয়া মিয়া [১৮৬৪-৮৩] এবং খান বাহাদুর মাইনউদ্দিন আহমদ [১৮৮৩-১৯০৬] যথাক্রমে ফরায়েজী আন্দোলনের নেতা মনোনীত হন।
শেষোক্ত মাইনউদ্দিন আহমদ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন সমর্থন করেন। সাইফুদ্দিনের পর তাঁর পুত্র আবু খালেক রশিদ উদ্দিন ওরফে বাদশা মিয়া ফরায়েজীদের ওস্তাদ মনোনীত হন।
তিনি খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারাবরণ করেন।
জীবনের শেষপ্রান্তে তিনি পাকিস্তান আন্দোলনে যোগ দেন।
বাদশা মিয়া ১৯৫১ সালের ১৩ ডিসেম্বর ইন্তিকাল করেন।
১৯৪৭ সালে বৃটিশ শাসনের অবসান ও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর তিনি তাঁর অনুসারীদের ঈদের নামায আদায়ের অনুমতি দেন।”
মুন্শী আবদুল মান্নান তার প্রবন্ধে উল্লেখ করেন-
“পলাশী বিপর্যয়ের [১৭৫৭ সালের ২৩শে জুন] মধ্য দিয়ে কার্যত বাংলার মুসলিম শাসনের অবসান সূচিত হয়।
পরবর্তীতে নামকাওয়াস্ত কয়েকজন নবাবের আবির্ভাব ঘটলেও এরা সবাই ছিলেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর হাতের ক্রীড়নক মাত্র।
এদের মধ্যে একমাত্র নবাব মীর কাসিমই উপলব্ধি করতে পারেন যে, বাংলার এত দিনের মুসলিম শাসন মারাত্মকভাবে বিপন্ন হয়ে পড়ছে।
তিনি পলাশী ট্রাজেডির আট বছরের মধ্যে অর্থাৎ ১৭৬৪ সালে স্বাধীনতা সুরক্ষা বা পুনরুদ্ধারের জন্য কোম্পানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন।
‘বক্সারের যুদ্ধ’ নামে পরিচিত এই যুদ্ধে তাঁর শোচনীয় পরাজয় ঘটে।
ঐতিহাসিকদের মতে, এটা পরাজয়ের মধ্য দিয়ে প্রকৃত ক্ষমতা ও পূর্ণ কর্তৃত্ব কোম্পানীর হাতে চলে যায়।
রাজনৈতিক ক্ষমতাও তাদের করতলে চলে গিয়েছিল।
১৭৬৫ সালে দেওয়ানী গ্রহণের মধ্য দিয়ে নিরংকুশ ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অধিকারী হয়ে যায় কোম্পানী।
এই পরিবর্তনের ফলে কেবল স্বাধীন নবাব বিদেশীদের শাসনে আবদ্ধ হলেন না, একই সাথে শাসক মুসলমান শাসিতের শ্রেণীতে পরিণত হয়ে গেল।
যেহেতু মুসলমানদের হাত থেকেই ক্ষমতা ছিনিয়ে নেয়া হয়, সুতরাং মুসলমানরাই নব্য শাসকদের সর্বপ্রকার অন্যায়, জুলূম, পীড়ন ও শোষণের শিকারে পরিণত হয়।
কোম্পানী মুসলমানদের রাজনৈতিক, সামরিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে উৎখাত করার দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হয় এবং একে একে এই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে।
প্রথমেই নব্য শাসকরা দ্বিমুখী নীতি গ্রহণ করে।
মুসলমানদের সরারী বা রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ পদ থেকে সরিয়ে দেয়।
তাদের স্থলে প্রতিবেশী হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকদের নিয়োগ করে।
অর্থনৈতিক ও অন্যান্য ক্ষেত্রে এদের সুযোগ-সুবিধা দিয়ে পুরোপুরি নিজেদের দলে ভিড়িয়ে নেয়।
লাখেরাজ ও আয়মা সম্পত্তি থেকে মুসলিমদের বঞ্চিত করা হয়।
বিভিন্ন প্রকার নিপীড়নমূলক কর তাদের ওপর ধার্য করা হয়।
সরকার ও সেনাবাহিনী থেকে মুসলমানদের অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে সরিয়ে দেয়া হয়।
এক হিসাব থেকে দেখা যায়, ১৭৫৭ থেকে ১৭৬৫ সালের মধ্যে কেবল সামরিক বাহিনী থেকেই ৮০ হাজার মুসলমানকে তাড়িয়ে দেয়া হয়।
১৭৫৭ সালের পট পরিবর্তনেরপর সর্বব্যাপী এমন এক শোষণ, পীড়ন ও নাশকতার উদ্ভব ঘটে যে, ১২ বছরের মাথায় স্মরণকালের সবচেয়ে বিভীষিকাময় দুর্ভিক্ষ নেমে আসে গোট বাংলায়।
ইতিহাসে ছিয়াত্তরের [বাংলা ১১৭৬ সন] মন্বন্তর নামে চিহ্নিত এই মহাদুর্ভিক্ষে লাখ লাখ মানুষের খাদ্যাভাবে অসহায় মৃত্যু ঘটে।
জমিদারের খাজনা, নীলকরদের অমানুষক নির্যাতন, মহাজনের দেনার চাপ এবং শাসকদের শোষণ-শাসন-পড়নে যখন জনগণ বিপন্ন ও দিশাহারা ঠিক তখনই এই মন্বন্তর আঘাত হেনে গোটা বাংলাকে প্রায় গোরস্তানে পরিণত করে।
এরপর ১৭৭২ থেকে ১৭৭৩ সালের মধ্যে কোম্পানী যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চাপিয়ে দেয়, তা ‘মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা’ হয়ে দাঁড়ায়।
১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের ফলে ভূীম ব্যবস্থায় যে পরিবর্তন ঘটে, তাতে বাংলার কৃষক সাজ বস্তুত ভূমিদাসে পরিণত হয় এবং কৃষক সমাজের অর্থনৈতিক অবস্থা পুরোপুরি ভেঙ্গে পড়ে।
অপরদিকে মুসলিম জমিদার তালুকদাররা জমিদারী-তালুকদারী হারিয়ে সর্বস্বহীন হয়ে পড়ে এবং তাদের জমিদারী-তালুকদারী তাদেরই নামের গোমস্তারা হস্তগত করে নেয়।
এদের অধিকাংশই ছিল কোম্পানীর সহযোগী-সহায়তাকারী হিন্দু সমাজের অন্তর্গত।
শুধু তাই নয়, ডাকাত-দস্যুরা পর্যন্ত কোম্পানীর শাসকদের অনুকুল্যে রাতারাতি ‘রাজা’ মহারাজা’ বনে যায়।
দস্যু দলপতি দেবী সিংয়ের ‘রাজা’ হওয়ার কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়।
দেবী সিংহ শুরুতে খাজনা আদারে ইজারাদারী লাভ করে।
দুর্ভিক্ষের সময় খাজনা আদায়ের নামে এই দেবী সিং উত্তরবঙ্গের কৃষকদের ওপর এমন নিপীড়ন ও অত্যাচার চালায় যে, হাজার গ্রাম জনশূন্য হয়ে পড়ে।
পরবর্তীতে দেবী সিং রাজা উপাধি পায় এবং বিরাট জমিদারী পত্তন করে। বাংলা কৃষিনির্ভর আর্থ-সামাজিক কাঠামোর ওপর দাঁড়িয়ে থাকলেও শিল্পক্ষেত্রে পিছিয়ে ছিল না।
সমকালীন বিশ্বে শিল্পক্ষেত্রে বাংলার বিশিষ্ট স্থান ও অবস্থান ছিল।
সেই সময় ঢাকাই মসলিনের খ্যাতি ছিল বিশ্বজোড়া।
বস্ত্র ছাড়াও বিভিন্ন পণ্য রফতানী করে বাংলা প্রতি বছর বিপুল বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতেন।
শাসকগোষ্ঠী নানা কৌশল ও ষড়যন্ত্র করে এই শিল্পকেও ধ্বংস করে দেয়। এক হিসাবে দেখা যায়, ১৭৮৭ সালে কেবল ঢাকা থেকেই ৩০ লাখ টাকার মসলিন ইংল্যান্ডে রফতানী হয়।
মুসলিম ব্যবসায়ী ও শিল্পীদের ওপর অপরিসীম জুলুম, শোষণ ও নির্যাতন চালিয়ে এমন কি শিল্পীদের আঙ্গুল কেটে দিয়ে এই শিল্পের অস্তিত্ব বিরৈা করে দেয়া হয়।
দেখা যায়, কোম্পানী শাসন প্রতিষ্ঠার ৫০ তেকে ৭০ বছরের মধ্যে বাংলার মুসলমান সমাজ, আর্থ, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয়- সকল ক্ষেত্রে পতিত হয়ে পড়েছে।
বিপদ-বিপর্যয়ের তাদের সীমা-পরিসীমা নেই।
তাদের অস্তিত্ব হয়ে পড়েছে মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন।
রাজনৈতিক ও আর্থিক দুরবস্থার সুবাদে বাংলার জনসমাজের নিম্নতম অবস্থানে এসে দাঁড়িয়েছে গরিষ্ঠ সংখ্যার অধিকারী মুসলমানরা।
অনিবার্যভাবে ধর্মীয় সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও তারা দিক-দিশাহীন গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়েছে।
সুদীর্ঘকাল ধরে হিন্দু সমাজ সম্প্রদায়ের পাশাপাশি বসবাস করার কারণেই মুসলমান সম্প্রদায় সমাজের কোন কোন স্তরে বা পর্যায়ে হিন্দু আচার-সংস্কৃতির প্রভাব পড়েছিল।
রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক অবস্থান হারানোর বিপর্যয়ের মধ্যে এই প্রভাব ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করার সুযোগ পায়।
যার ফলে মুসলমানসমাজে শিরক, বিদয়াত ও অনৈসলামিক আচার-প্রথা এমন এক অবস্থায় আধিপত্য বিস্তার করে যে, পৃথক পরিচয়ে মুসলমান চিহ্নিত করাই দুরূহ হয়ে পড়ে।
মুসলমানদের মধ্যে পীর পূজা, মাজার পূজা ব্যাপক প্রচলন ঘটে।
হিন্দুদের ভূত-প্রেত বিশ্বাস তাদের বিশ্বাসেও পরিণত হয়।
হিন্দুদের বিভিন্ন পূজা, যেমন- গো পূজা, শীতলা দেবীর পূজা, মনসা পূজা ইত্যাদি মুসলিম সমাজেও প্রতিষ্ঠা লাভ করে।
হিন্দুদের দুর্গা পূজার আদলে তাজিয়া মিছিল ও তাজিয়া বিসর্জনের প্রথাও প্রচলিত হয়।
অর্থাৎ তৌহিদাবাদী ধর্মীয় সম্প্রদায় হিসেবে মুসলমানদের পরিচয় ও অস্তিত্বে মুছে যাওয়ার পর্যায়ে এসে দাঁড়ায়।
ঠিক এই পটভূমি ও পরিস্থিতিতে ইসলামের অবিনশ্বর জ্যোতিতে উদ্ভাসিত এক মহান ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটে পতিত ও বিলিয়মান এই মুসলিম সমাজে। তাঁর নাম- আল্লামা হাজী শরীয়তুল্লাহ।
তিনি পতিত স্বধর্মীয় সমাজ উদ্ধারে এবং ব্যক্তি পর্যায়ে ও সমাজের সর্বস্তরে মহান ইসলামের আলো ছড়িয়ে দেবার শপথ গ্রহণ করে সংস্কারবাদী আন্দোলনের সূচনা করেন, যার নাম- ‘ফরায়েজী আন্দোলন।’..
হাজী শরীয়তুল্লাহ যথার্থই উপলব্ধি করেন যে, মুসলমানদের এই অধঃপতন, দুর্গতি ও বিপর্যয়েল প্রধান কারণ বিদেশী ও বিধর্মীয় দুঃশাসন।
এই দুঃশাসনের অবসান ঘটিয়ে স্বাধীনতা ও স্বশাসন কায়েম করা ছাড়া দেশ ও দেশবাসীর মুক্তি- বিশেষত মুসলমানদের স্বগৌরবে অস্তিত্বের পুনঃপ্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়।
বিদেশী-বিধর্মীয় শাসন উৎখাতের জন্য ‘জিহাদ’ ছাড়া কোনো বিকল্প নেই। এই উপলব্ধি থেকে তিনি ঘোষণা দেন:
‘এদেশ শত্রু কবলিত রাষ্ট্র।
ইংরেজ ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে অবৈধভাবে দেশ শাসন করছে। সুতরাং তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করে দেশকে স্বাধীন করা জনগণের একটি বৈধ অধিকার এবং এটি দেশবাসীর একটি পবিত্র দায়িত্ব।’
তাঁর এই দু’টি ঘোষণা নির্যাতিত, নিপীড়িত, শোষিত মুসলমানের মধ্যে উদ্দীপনার সৃষ্টি করে।
পক্ষান্তরে শাসক ও জমিদার শ্রেণর মধ্যে বিরাট আশংকা ও উব্দেগ সঞ্চার করে।
ঢাকা জেলার নয়াবড়ী নামক স্থানের কেন্দ্র করে তিনি তাঁর আন্দোলন শুরু করেন।
অল্প কিছুদিনের মধ্যে ঢাকা, পাবনা, বরিশাল, নদীয়া, মোমেনশাহী প্রভৃতি অঞ্চলে এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে।
তিনি গ্রামে গ্রামে গিয়ে কৃষকদের সংগঠিত করেন এবং ইসলারেম ফরজ প্রতিষ্ঠা, বিদেশী-বিধর্মিদের শাসন উৎখাতের এবং জমিদার ও শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানান।
জনগণ পর্যায়ে- বিশেষত কৃষক তাঁতী সম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁর আন্দোলন ব্যপকভাবে বিস্তার লাভ করে।
তিনি তাদের পথ প্রদর্শক ও অবিসংবাদী নেতায় পরিণত হন।
হাজী শরীয়তুল্লাহ দেশকে ‘দারুল হরব’ বা জিহাদের মাধ্যমে এই শত্রু শাসনউৎখাত করে দেশকে ‘দারুল ইসলাম’ বা ইসলামের আলোয় হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার স্বপ্ন দেখেছিলেন এবং এই স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্যে তাঁর আন্দোলন ছিল উড়ে এসে জুড়ে বসা কোম্পানী শাসকদের বিরুদ্ধে এবং জমিদার মহাজনদের বিরুদ্ধে।
ফলে তারাই যুগপৎভাবে তাঁর বিরুদ্ধে সকল শক্তি নিয়োজিত করেছিল।
কিভাবে হাজী শরীয়তুল্লাহকে সরানো যায়, কেমন করে তাঁকে শায়েস্তা করা যায়- এসব চিন্তা-ভাবনা ও ষড়যন্ত্র একই সাথে চলতে থাকে।
এই পর্যায়ে যখন নয়াবাড়ীর জমিদার ও স্থানীয জোতদারদের সাতে হাজী শরীয়তুল্লাহর সরাসরি বিরোধ দেখা যেদয়, তখন তাঁকে গ্রেফতার করা হয় এবং পরে নয়াবাড়ী থেকে বিতাড়িত করা হয়।
তিনি তাঁর সূচিত আন্দোলনের পূর্ণ সাফল্য দেখে যেতে পারেননি।
১৮৪০ সালে মাত্র ৫৯ বছর বয়সে এই মর্দে মুজাহিদ, কৃষক বন্ধু, স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্রসাধক এবং দারুল ইসলাম প্রতিষ্ঠার স্বপ্নদ্রষ্টা ইন্তিকাল করন।
পরবর্তীকালে ফরায়েজী আন্দোলনের নেতৃত্ব দান করেন তাঁর সযোগ্য পুত্র মোহসিন উদ্দিন।
সিপাহী বিদ্রোহ পর্যন্ত এই আন্দোলন প্রবলভাবে অব্যাহত থাকে।”
এই দুটি পুনর্মূল্যায়নই আমাদের ইতিহাসের জন্য যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি গুরুত্বপূর্ণ হাজী শরীয়তুল্লাহকে জানা ও বুঝার ক্ষেত্রেও।
হাজী শরীয়তুল্লাহ এবং তাঁর সংগ্রামী জীবন যে কত বিশাল-ব্যাপক ছিল, তার তুলনা তিনি নিজেই।
তার সেই বিশাল ভূমিকা ও ইতিহাস আমাদের সাহস ও উদ্দীপনা সৃষ্টির জন্য বার বার সামনে মেলে ধরা প্রয়োজন।
কেননা ৩৮ বছর বয়সে হাজী শরীয়তুল্লাহ তাঁর ফরায়েজী আন্দোলন শুরু করেছিলেন।
সারা জীবন তিনি এখানকার মানুষের মুক্তির সংগ্রামই করে গেছেন।
ফরায়েজী আন্দোলন শুধু ধর্মীয়রূপেই ছিল না, সেই সাথে এটা ছিল আর্থ-সামাজিক ও সংস্কার আন্দোলন।
ইসলামই ছিল এখানে প্রধান ভূমিকায়।
ইসলাম যে কোনো ধরনের অত্যাচারের বিরুদ্ধে এবং শোষিত জনগণের পাশে থাকে, তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্তই রেখেছিলেন হাজী শরীয়তুল্লাহ!
সেই আদর্শই পরবর্তীকালে আরো বিকশিত হয়েছে।
ইন্তিকাল
হাজী শরীয়তুল্লাহ ছিলেন বাংলার মুসলমানদের জন্যে এক সাহসী পুরুষ! তাঁর সমগ্র জীবনটাই ছিলো সংগ্রামের এক দীপ্তশিখা।
তিনি ছিলেন মুসলমানদের জন্যে, সেই চরম দুঃসময়ে একজন নির্ভরযোগ্য অভিভাবক।
ছিলেন সত্যের সৈনিক।
তাঁর হৃদয়ে ছিলো ইসলামের জন্যে অফুরন্ত ভালোবাসা।
অঢেল প্রেম ছিলো তাঁর দেশের জন্যে।
মানুষের জন্যে।
আর তাই তাদেরকে আঁধার থেকে আলোয় আনার জন্যে হাজী শরীয়তুল্লাহ সারাটি জীবন অপ্রাণ চেষ্টা করে গেছেন।
আঠারো শো চল্লিশ সাল।
দিনটি ছিলো আঠাশে জানুয়ারী।
দীর্ঘ সংগ্রামী জীবনের অবসান ঘটিয়ে এই বছর বিদায় নিলেন বাংলার প্রাণপ্রিয় নেতা, ইসলামী আন্দোলনের এক নির্ভীক ও নিবেদিত মুজাহিদ - হাজী শরীয়তুল্লাহ।
ইন্তিকালের পর তাঁর প্রিয় জন্মভূমি ফরিদপুরের শামাইলে ঘুমিয়ে আছেন তিনি।
সত্যিই কি ঘুমিয়ে আছেন?
না! এইতো শত বছর পরও আমাদের চেতনার দুয়ারে বার বার কড়া নেড়ে যাচ্ছেন একজন।
আমাদের সংগ্রামে, আমাদের জাগরণে, আমাদের অনুভবে এবং আমাদের চলার পথে তিনি আছেন সাহসের মশালহাতে নিয়ে!
আমাদের সকল সংগ্রাম ও আন্দোলনের প্রেরণার উৎস হিসেবে জেগে আছেন হাজী শরীয়তুল্লাহ!
তাঁর মতো ক্ষণজন্মা পুরুষেরা কখনো মরেন না।
তাদের কোনো মৃত্যু নেই।
যুগ যুগ ধরে বেঁচে থাকেনতাঁরা মানুষের চেতনায়।
মানুষের ভালোবাসায়। মানুষের শ্রদ্ধায়।
যেমন বেঁচে আছেন আমাদের সংগ্রামের উজ্জ্বল পুরুষ- হাজী শরীয়তুল্লাহ!
ফরায়েজী আন্দোলন নিয়ে
কৃষক কবিদের পুঁথি থেকে
“মহরমে এমামহাছেন হোছেনের।
হায় হায় জারি ছিল মশরেকগণের।
পাঁচ পীরের নামেতে মোকাম উঠাইয়া
উপবাস করিত সে সকলে মিলিয়া
...................
লাগাছ গাড়িত বাড়ীর চারিধার।
সেসব বেদাত এসে হইল মেছমার।
হাজি শরীয়তুল্লঅহ হেথা তশরিফ আনিয়া।
দীন জারি করিলেন বাঙ্গালা জুড়িয়া।
বংশ তালিকা
হাজী শরীয়তুল্লাহ (১)
মোহসেন উদ্দীন আহমদ (দুদু মিয়া) (২) (জন্ম: ১৮১৯, মৃত্যু ১৮৬২)
মাওঃ গিয়াস উদ্দীন হায়দার
আঃ গাফফার (নয়া মিয়া) মৃত্যু-১৮৮৪
সাঈদ উদ্দীন আহমদ (৩) মৃত্যু-১৯০৬
আবা খালেদ রশীদ উদ্দীন আহমদ (৪) (পীর বাদশাহ মিয়া) মৃত্যু-১৯৬০
আবু ওয়অছে রাজিউদ্দীন আহমদ (নওয়াব মিয়া)
আবুল হাফজ মোহসেন উদ্দীন আহমদ (দুদু মিয়া) (৫)
আবু ইয়াহ্ইয়অ মহিউদ্দীন আহ দ (দাদা মিয়া)
আবুল কালাম মঈনুদ্দীন আহমদ (জোবায়ের)
খলিল উল্লাহ (হুমায়ুন)
সালাহউদ্দীন ্াহমদ
আদনান আহমদ
তুরহান আহমদ
সোহেলকাদার
ইউসুসুফ কাদার
পাপ্পু
আবুল হাসানাত মোহসলেহ উদ্দীন আহমাদ (আবা বকর)
মোয়াজ্জে উদ্দীন আহমাদ (মাহমুদ)
আবু হাসান (শোয়াইব)
হাসিব উদ্দীন আহমদ
শরফুদ্দীন আহমদ (জোনায়েদ)
রাজী উদ্দীন আহমাদ (আবা বকর) বেনে আমীন)
রশীদ উদ্দীন আহমাদ (ইয়াহইয়অ)
মহীব উদ্দীন আহমাদ (মুনাদ)
মবিন উদ্দীন আহমদ (নওশি)
হাজী শরীয়তুল্লাহ : বিলুপ্ত কবরের এপটাফ
রাজধানী কেন্দ্রস্থলে বংশালে জীর্ণ অবস্থায় পড়ে আছে ফরায়েজী আন্দোলনের দ্বিতীয় পুরুষ দুদু মিয়ার কবরটি।
', 'হাজী শরীয়তুল্লাহ', '', 'publish', 'closed', 'closed', '', '%e0%a6%b9%e0%a6%be%e0%a6%9c%e0%a7%80-%e0%a6%b6%e0%a6%b0%e0%a7%80%e0%a7%9f%e0%a6%a4%e0%a7%81%e0%a6%b2%e0%a7%8d%e0%a6%b2%e0%a6%be%e0%a6%b9', '', '', '2019-10-24 13:26:24', '2019-10-24 07:26:24', '
হাজী শরীয়তুল্লাহ
মোশাররফ হোসেন খান
স্ক্যান কপি ডাউনলোড
আগের কথা
সতেরো শো সাতান্ন সাল।
মীর জাফরদের চক্রান্তে ইংরেজদের কাছে পরাজিত হলেন বাংলার নবাব সিরাজদ্দৌলাহ।
পলাশীর প্রান্তরে নবাব সিরাজদ্দৌলার পরাজয়ের পর বাংলার মুসলমানদের ভাগ্যাকাশে দেখা দেয় এক ভয়ংকর সর্বনাশের ঘনঘটা।
ইংরেজ এবং উগ্র হিন্দুদের হাতে জিম্মি হয়ে পড়ে বাংলার মুসলমান। রাজনৈতিক, ঐতিহ্যিক এবং সাস্কৃতিক ক্ষেত্রে মুসলমানরা এ সময়ে যেমন ইবংরেজ ও হিন্দুদের উৎপীড়নের শিকার হয়, তেমনি তাদের নির্মমতার শিকার হয়ে অর্থনৈতিকভাবে তারা দুর্বল ও নিঃস্ব হয়ে পড়ে।
মুর্শিদকুলী খানের আমল থেকেই হিন্দুরা মুসলিম শাসন উৎখাত করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলো। ইংরেজ ব্যবসায়ীদের সাথে তাদের সম্পর্ক ছিলো অত্যন্ত নিবিড়।
সতেরো শো ছত্রিশ সাল থেকে সতেরো শো চল্লিশ সালের মধ্যে ইংরেজ কোম্পানী- কলকাতায় বায়ান্নজন ব্যবসায়ী নিয়োগ করেছিলেন। তাদের সবাই ছিলো হিন্দু। সতেরো শো ঊনচল্লিশ সালে কাশিম বাজারে তারা পঁচিশজন ব্যবসায়ী নিয়োগ করে। তারাও ছিলো হিন্দু।
এ সময়ে মুসলমানদের কোথাও স্থান ছিলো না। না ব্যবসায় বাণিজ্যের ক্ষেত্রে। না চাকরীর ক্ষেত্রে। যাদের আগে থেকেই চাকরি ছিলো, তাদেরকেও বাদ দেয়া হলো।
এই চরম দুঃসময়ে লাখ লাখ মুসলমান বেকারত্বের অভিশাপ নিয়ে যাত্রা করলো গ্রামের দিকে। উদ্দেশ্য ছিলো, কৃষিকে আঁকড়ে ধরে কোনো রকমে বেঁচে থাকা।
গ্রামের অবস্থা ছিলো আরো ভয়াবহ।
শাসন ক্ষমতা হস্তগত করার সাথে সাথে ইংরেজ বণিকরা বাংলার প্রাচীন গ্রামের ভিত্তি ভূমিকে ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছিলো। ভেঙ্গে দিয়েছিলো তারা গ্রামের সমাজ কাঠামোকেও। এ কাজে তারা প্রধানত দু’টি অস্ত্র ব্যবহার করলো- ভূমি রাজস্বের নতুন ব্যস্থা ও ভূমি রাজস্ব হিসেবে ফসল বা দ্রব্যের পরিবর্তে মুদ্রার প্রচলন।
এই দুই অস্ত্রের প্রচণ্ড শক্তির আঘাতে স্বল্পকালের মধ্যে প্রাচীন গ্রাম-বাংলার ভিত্তি একেবারে ধূলিসাৎ হয়ে গেলো। শ্মসানে পরিণত হলো হাজার হাজার গ্রাম।
বহুমুখী শোষণ-উৎপীড়নের চাপে পড়ে বাংলার অসহায় কৃষক সমাজ নিঃস্ব হয়ে অনিবার্য ধ্বংসের মুখে এসে দাঁড়ালো।
বাংলার দরিদ্র কৃষক মানেই মুসলমান। আর জমিদার এবং বিত্তবান মানেই হিন্দু।
ক্ষমতা হারিয়ে, চাকরি খুইয়ে মুসলমানরা যখন দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে হতাশাগ্রস্ত, তখন ইংরেজ সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় সর্বস্তরে ক্ষমতা সম্পদের অধিকারী হলো হিন্দু দেওয়ান, গোমস্তা, বেনিয়ান, মুৎসুদ্দিরা। সকল ক্ষেত্রে তখন হিন্দুদেরই একচ্ছত্র দাপট।
কর্নওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বদৌলতে জমির মালিকরূপে পরিগণিত হলো হিন্দুরাই। শুধামাত্র অর্থগুণে দেব, মিত্র, সিংহ, মল্লিক, শীল এমন কি তিলি আর সাহা-রাও রাতারাতি জমিদাররূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করলো।
পুরনো জমিদারদের অনেকেই নানা কারণে জমিদারী বিক্রি করেছিলো। সেই জমিদারী কিনে নিয়েছিলো সম্পদশালী হিন্দু ব্যবসায়ীরা।
নব্য জমিদারদের খাজনা ও বহুবিধ করের চাপের এবং জমিদারদের নিয়োগকৃত নায়েব গোমস্তাদের রোষেপড়ে গরীব চাষীরা হলো এবার ভিটেছাড়া।
একদিকে জমিদার মহাজনের শোষণ-পোড়ণ আর আধুনিক অত্যাচার, অপরদিকে কুশিখ্ষা, অশিক্ষার অভিশাপ। তার ওপর আছে রোগ, মহামারী ও দুর্ভিক্ষ। এ সবকিছু মিলিয়ে মুসলিম চাষীরা এমন এক করুণ ও ভয়াবহ অবস্থার শিকার হলো- যার পরিণতি ছিলো অনিবার্য ধ্বংস।
সরকারী চাকরি পাওয়ার সকল দরোজা বন্ধ হয়ে গেলো মুসলমানদের জন্যে। তাদের মধ্যে যারা ইংরেজী শিখে যোগ্যতা অর্জনের চেষ্টা করলো- তারাও চাকরি পেলো না। কেননা চাকরির বিজ্ঞাপনে তখন স্পষ্ট উল্লেখ থাকতো কেবল হিন্দু প্রার্থদেরই আবেদন গ্রহণযোগ্য।
‘দূরবীন’ নামক কলকাতার একটি ফরাসী পত্রিকা ছিলো।
আঠারো শো ঊনসত্তর সালের জুলাই মাসে চাকরির ক্ষেত্রে মুসলমানদের দুর্দশার কথা বর্ণনা করতে গিয়ে ‘দুরবীন’ পত্রিকাটি লিখেছিলো:
“উচ্চস্তরের বা নিম্নস্তরের সমস্ত চাকরি ক্রমান্বয়ে মুসলমানদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে, বিশেষ করে হিন্দুদের মধ্যে বিতরণ করা হচ্ছে। সরকার সকল শ্রেণীর কর্মচারীকে সমান দৃষ্টিতে দেখতে বাধ্য, তথাপি এমন সময় এসেছে যখন মুসলমানদের নাম আর সরকারী চাকুরিয়াদের তালিকায় প্রকাশিত হচ্ছে না, কেবল তারাই চাকরির জায়গায় অপাংক্তেয় সাব্যস্ত হয়েছে। সম্প্রতি সুন্দরবন কমিশনার অফিসে কতিপয় চারিতে লোক নিয়োগের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়, কিন্তু অফিসাপরটি সরকারী গেজেটে কর্মখালির যে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেন তাতে বলা হয় যে, “শূণ্য পদগুলিতে কেবলমাত্র হিন্দুদের নিয়োগ করা হবে।”
তখনকার দিনে অফিস আদালত ও পুলিশ বিভাগেও কেবলমাত্র হিন্দুদেরকে নিয়োগ করার নির্দেশ দেয়া হতো।
শুধা চাকরি নয়। শিক্ষা ও ব্যবসার ক্ষেত্রেও মুসলমানদের অবস্থা ছিলো দুর্ভাগ্যজনকভাবে সংকটময়।
অপরদিকে ধর্মীয়ভাবেও মুসলমানরা ছিলো অনগ্রসর। ইসলাম থেকে, ইসলামের মূল শিক্ষা ও আদর্শ থেকে তারা অনেক অনেক দূরে সরে গিয়েছিলো।
হিন্দুদের পাশাপাশি দীর্ঘকাল বসবাস করার কারণে এবং অসচেতন থাকার ফলে তারা শিরক ও বিদআতের মতো বড়ো বড়ো গুনাহের কাজে লিপ্ত থাকতো। হিন্দুয়ানী অপসংস্কৃতির জোয়ারে ভেসে গিয়েছিলো তখনকার অধিকাংশ মুসলিম পরিবার।
ঠিক এমনি এক ক্রান্তিকালে, এমনি এক অস্থির দুঃসময়ে জন্মলাভ করলেন এই উপমহাদেশের সংগ্রামী নেতা- হাজী শরয়তুল্লাহ।
জন্ম ও শৈশব
সতেরো শো একাশি সাল।
দিনিটির কথা কেউ আর বলতে পারে না।
এই বছরের কোনো একদিনে হাজী শরীয়তুল্লাহ জন্মলাভ করেন। গ্রামের নাম শামাইল।
গ্রাটি ছিলো বর্তমান মাদারীপুর জিলার বাহাদুরপুরের অন্তর্গত।
তাঁর জন্ম হয়েছিলো একটি প্রখ্যাত জমিদার পরিবারে।
শরীয়তুল্লাহর আব্বার নাম আবদুল জলিল তালুকদার।
তিনি ছিলেন একজন বিখ্যাত ব্যক্তি।
তা৭র নাম ডাক ছিলো চারদিকে।
তিনি ছিলেন যেমনি ভদ্র, তেমনি দয়ালূ। এ কারণে সবাই তাঁকে ভালোবাসতো প্রাণ দিয়ে।
শরীয়তুল্লাহর পিতা আবদুল জলিল ছিলেন একজন প্রজাবৎসল তালূকদার। অন্যান্য তালুকদারের মতো তিনি সাধারণ প্রজাদের ওপর জুলুম-নির্যাতন চালাতেন না।
শোষণের কুড়াল মারতেন না প্রজাদের মাথায়।
তিনি ছিলেন তাদের প্রতি অত্যন্ত দয়ালূ।
সাধারণ প্রজাদের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নার সাথে আবদুল জলিল নিজেকেও যুক্ত করতেন। শরীক হতেন তাদের ব্যাথা-বেদানার সাথে
সমবেদনা জানাতেন। সাহায্য করতেন সাধ্য মতো। এজন্যে তাঁর নামটি ছড়িয়ে পড়েছিলো অনেক দূর পর্যন্ত।
সবাই তাঁকে শ্রদ্ধা করতো। সম্মান দেখাতো।
শরীয়তুল্লাহ এই বিখ্যাত ও সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।
আবদুল জলিল তালুকদার চেয়েছিলেন- তাঁর ছেলেও হবে মানুষের মতো মানুষ।
সে হবে শিক্ষিত এবং আদর্শবান।
সাধারণ মানুষের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করবে সে।
শরীয়তুল্লাহ শৈশবে বর্ণজ্ঞান লাভ করে তাঁর পরিবারের কাছে। তারপর গ্রারেম মক্তবে।
পিতার ইচ্ছা ছিলো শরীয়তুল্লাহর শিক্ষা জীবনের সফলতা নিজের চোখে দেখে যাবেন।
কিন্তু তিনি সে সময় আর পাননি।
শরীয়তুল্লাহ এবং এক কন্যা সন্তানকে শিশু অব্থায় রেখে ইন্তেকাল করলেন আবদুল জলিল তালুকদার।
আবদুল জলিল তালুকদারের ছিলেন আরও দুই ভাই।
এক ভাইয়ের নাম মুহাম্মদ আজিম। তিনি শামাইল গ্রামেই থাকতেন।
অপর ভাই মুহাম্মদ আশেক। থাকতেন মুর্শিদাবাদ। তিনি মুর্শিদাবাদের নবাবের দরবারে মুফতি ছিলেন।
তিনি ছিলেন মস্ত বড়ো এক আলেম।
পিতার ইন্তিকালের পর বালক শরীয়তুল্লাহর লালন-পালন এবং শিক্ষার দায়িত্বগ্রহণ করলেন আপন চাচা মুহাম্মদ আজিম। তিনি ছিলেন নিঃসন্তান। মুহাম্মদ আজি আপন সন্তানের মতোই আদর যত্নে লালন করছিলেন শরীয়তুল্লাহকে।
অসীম স্নেহ আর ভালোবাসায় তিনি ভরে দিতেন শরীয়তুল্লাহর শিশুমনকে। কিন্তু শরীয়তুল্লাহর শিক্ষার ব্যাপারটি ছিলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ
তখন গ্রামে ছিলো না ভালো কোনো স্কুল, মাদরাসা। ছিলো না তেমন কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। সুতরাং শিক্ষা লাভের জন্যে অবশ্যই দূরে কোথাও যেতে হবে।
কিন্তু কোথায় যাওয়া যায়?
একান্তে ভাবেন কিশোর শরীয়তুল্লাহ!
কলকাতায় গমন
শিক্ষার প্রতি ছিলো বলক শরীয়তুল্লাহর অদম্য আগ্রহ।
এই আগ্রহের কারণে অল্প বয়সেই শরীয়তুল্লাহ পাড়ি জমালেন শামাইল থেকে সুদূর কলকাতা।
তাঁর এই সিদ্ধান্তে চাচা আজিমও খুব খুশি হলেন। কারণ তিনিও চান মানুষের মতো মানুষ হোক আদরের শরীয়তুল্লাহ।
সালীট ছিলো সতেরো শো তিরানব্বই।
কলকাতায় গিয়ে শরীয়তুল্লাহ ওঠেন মাওলানা বশারত আলীর কাছে।
মাওলানা বশারত আলী ছিলেন এক মস্ত বড়ো আলেম। ছিলেন পাক্কা দীনদার।
বালক শরীয়তুল্লাহর শিক্ষার প্রতি অসম্ভব আগ্রহ দেখে তিনি খুব খুশি হলেন। অত্যন্ত আন্তরিকতা ও স্নেহের সাথে তিনি শরীয়তুল্লাহর সামনে তুলে ধরলেন শিক্ষা ও জ্ঞানের প্রদীপ।
শরীয়তুল্লাহও ছিলেন অত্যন্ত শান্ত ও মেধাবী। ভদ্রতা ছিলো তাঁর সকল সময়ের ভূষণ।
একাগ্রতার সাথে তিনি মাওলানা বশারত আলীর কাছে পড়তে থাকলেন। শরীয়তুল্লাহর লেখাপড়ার প্রতি মনোযোগ দেখে এবং তাঁর চরিত্র-মাধুর্যে মোহিত হয়ে মাওলানা বশারত আলী তাঁর এই প্রিয় ছাত্রের লেখা-পড়ার যাবতীয় দায়িত্বভার তুলে নিলেন নিজের কাঁধে।
শরীয়তুল্লাহকে তিনি পরবর্তীতে ভর্তি করে দিলেন হুদলী মাদরাসায়। মাদরাসাটি ছিলো হুগলিরি ফুরফুরায়।
মাদরাসায় ভর্তি হবার পর শরীয়তুল্লাহ লেখা-পড়ায় আরও বেশী মনোযোগী হলেন।
দুর্ঘটনার কবলে
কলকাতায় মাওলানা বশরাত আলীর তত্ত্বাবধানে লেখা-পড়া করার সময় শরীয়তুল্লাহ একবার মুর্শিদাবাদ গেলেন।
সেখানে থাকেন চাচা মুফতী মুহাম্মদ আশিক।
চাচার সাথে সাক্ষাৎ করলেন শরীয়তুল্লাহ। এরপর থেকে তিনি প্রায়ই যেতেন চাচার কাছে। হৃদয়ের টানে।
চাচা ছিলেন অত্যন্ত কর্মব্যস্ত মানুষ।
এজন্য বহুদিন হলো আপন মাতৃভূমিতে আসার সুযোগ পাননি তিনি।
এর মধ্যে শরীয়তুল্লাহর ওপর দিয়েও গড়িয়ে গেছে অনেকটা সময়। তিনিও অনেকদিন যাবত বাড়ি ছাড়া।
যোগাযোগ নেই গ্রামের সাথে। গ্রামের মানুষ আর অবারিত সবুজের সাথে।
গ্রামে ফেরার জন্যে তাই মনটা তাঁর কেবলই আনচার করে ওঠে।
ব্যাকুল হয়ে ওঠে তাঁর কিশোর হৃদয়।
চাচা মুফতী আশক একদিন শরীয়তুল্লাহকে বললেন, চলো আমরা বাড়ি থেকে একবার বেড়িয়ে আসি।
কথাটি শুনার সাথে সাথে শরীয়তুল্লাহর চোখে আপন বাস্তু ভিচার ছবিটা ছবির মতো ভেসে উঠলো।
তাঁর হৃদয়টা দুলে উঠলো মুহূর্তেই।
তিনি রাজি হয়ে গেলেন চাচার কথায়।
মুর্শিদাবাদ থেকে রওয়ান হলেন তাঁরা। নৌকাযোগে আসছেন নিজ গ্রাম- ফরিদপুরেরর শামাইলে।
সাথে আছে চাচা ও চাচী। নৌকা চলছে গঙ্গার বুক দিয়ে। পানি কেটে কেটে।
শাঁ শাঁ গতিতে। প্রমত্তা গঙ্গ!
ভয়ঙ্কর তার স্রোত!
তার ওপর আকাশে মেঘ এবং ঝড়ের পূর্বাভাস। ওলোট পালোট বাতাস। ঝড়ের ইঙ্গিত! তবুও নৌকা চলছে প্রবল গতিতে।
হঠাৎ শুরু হয়ে গেলো গঙ্গার বুকে ঝড়েড় দপাদপি! সে কি ঝড়!
ঝড়ের কবলে পড়ে মুহূর্তেতই যাত্রী বোঝাই নৌকাটি তলিয়ে গেলো গঙ্গার বুকে! আর তারই সাথে গঙ্গার প্রচণ।ড স্রোতের তোড়ে চিরতরে হারিয়ে গেলেন চাচীজান। হারিয়ে গেলেও চাচাও।
হারিয়ে গেলেন একজন বিখ্যা আলেমে দীন- মুফতী আশিক।
গঙ্গা তখনো ফুঁসছে ক্রমাগত।
গঙ্গার সেই ভয়ালো ঝড় আর ঢেউকে উপেক্ষা করে আল্লাহর অসীম রহমতে সাঁতরিয়ে কূলে উঠে দাঁড়ালেন শরীয়তুল্লাহ!
অলৌকিক ব্যাপার বটে! প্রাণে বেঁচে গেলেণ তিনি।
মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে গিয়ে অশেষ শুকরিয়া জানালেন মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে।
কূরে উঠে তিনি গঙ্গার দিকে তাকিয়ে হতাশ হলেন। কেঁপে উঠলো তাঁর বুক!
শূন্যতায় ভরে গেলো তাঁর কোমল হৃদয়।
কূরে দাঁড়িয়ে তিনি গঙ্গার বুকে কোথাও খুঁজে পেলেন না চাচা, চাচী এবং সেই নৌকাটিকে!
ফরিদপুর আর আসা হলেঅ না শরীয়তুল্লাহর
দেখা হলো না আর প্রাণ-প্রিয় মাতৃভূমি শামাইল।
এক বুক বেদনা আর স্বজন হারানো কষ্ট নিয়ে তিনি আবারো ফিরে গেলেন কলকাতায়।
ফিরে গেলেন প্রিয় শিক্ষক মাওলানা বশারত আলীর কাছে।
কলকাতায় ফেরার পর শরীয়তুল্লাহর মুখ থেকে সকল কথা শুনলেন মাওলানা বশারত আলী।
শুনলেন তাঁর স্বজন হারানোর বেদনার কথা। নৌকাডুবির কথা।
তিনি শুনলেণ শরীয়তুল্লাহর আল্লাহর রহমতে অলৌকিকভাবে বেঁচে যাবার কথা।
সকল কথা শুনার পর মাওলানা বশারত আলী অবাক হলেন।
তিনি শরীয়তুল্লাহকে আরো বেশি আদর-স্নেহে কাছে টেনে নিলেন।
সতেরো শো নিরানব্বই সাল।
মাওলানা বশারত আলী মক্কায় যাবার সিদ্ধান্ত নিলেন।
মক্কায় যাবেন তিনি নবীজীর (সা) পবিত্র কবর মুবারক যিয়ারত করার জন্যে। শরীয়তুল্লাহকে সাথে নেবার ইচ্ছাও প্রকাশ করলেন তিনি।
কি সৌভাগ্য তাঁর!
এক অলৌকিকভাবে তাঁর মক্কা যাবার স্বপ্ন বাস্তবায়ন হতে যাচ্ছে!
তিনি ভাবতেই পারেননি এতো সহজে মক্কায় যেতে পারবেন।
আল্লহর কুদরত ও রহমতের শুকরিয়া জানিয়ে তিনি রাজি হয়ে গেলেন। রাজি হয়ে গেলেন মাওলানা বশারত আলীর প্রস্তাবে।
কিছু দিনের মধ্যেই শরীয়তুল্লাহ তাঁর প্রিয় শিক্ষক মাওলানা বশারত আলীর সাথে মক্কার পথে যাত্রা শুরু করলেন।
মক্কা জীবনে
মাওলানা বশারত আলীর সাথে মক্কায় আসার পর হাজী শরীয়তুল্লাহর বুকটা আনন্দে ভরে উঠলো।
তাঁর ছিলো শিক্ষার প্রতি অসম্ভব আগ্রহ।
তিনি মক্কাতেও শিক্ষালাভের জন্য অপ্রাণ চেষ্টা করলেন। শরীয়তুল্লাহ মক্কায় ছিলেণ একটা বিশ বছরের মতো।
অনেক দীর্ঘ সময়।
এই দীর্ঘ সময়ে তিনি মক্কার বহু বিখ্যাত শিক্ষকের কাছে পড়াশুনা করলেন। কিতাবী শিক্ষার পাশাপাশি তিনি ইসলামের ব্যবহারিতক দিক সম্পর্কেও সম্যক জ্ঞান লাভ করলেন।
যেহেতু মক্কায় গেছেন। সেই কারণে হজ পালন করাটা তো আর হাত ছাড়া করা যায় না!
শরীয়তুল্লাহ সাথে সাথে হজ পালনের পর্বটা সেরে নিলেন।
কি আশ্চর্যের বিষয়!
আপন সাধনা ও শ্রমের বলে হাজী শরীয়তুল্লাহ একজন উচ্চ শিক্ষিত আলেম হিসাবে সুদূর মক্কাতেও বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছিলেন।
বাংলাদেশথেকে মক্কা অনেক- অনেক দূরের পথ।
একটি ভিন্ন দেশ। ভিন্ন তাদের ভাষায়। ভিন্ন তাদের শিক্ষা ব্যবস্থাও শিক্ষাদান পদ্ধতি।
কিন্তু তা হলে কি হবে?
হাজী শরীয়তুল্লাহর খ্যাতি তখন মক্কার চারদিকে।
সেই খ্যাতির সৌরভে মৌ মৌ করছে মক্কার বিস্তৃত প্রান্তর।
ইসলাম সম্পর্কে তাঁর পাণ্ডিত্যের কথা তখন সবার মুখে মুখে।
তাঁর জ্ঞানের বহরের কথা মক্কার শিক্ষিত মানুষ মাত্রই জেনে গেছেন।
অবাক হবারই তো কথা!
তাঁর পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে সেখানকার মানুষ হাজী শরীয়তুল্লাহকে শিক্ষক নিযুক্ত করলেন।
হাজী শরীয়তুল্লাহ মক্কায় বিশ বছর অবস্থান করার সময়ে বেছে নেন শিক্ষকতার এই মহান পেশা।
তিনি মক্কার নামী-দামী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা করতে থাকেন।
এতে করে তাঁর সময়টা ভালোই কাটছিলো। আরো বৃদ্ধি পাচ্ছিলো তাঁর জ্ঞানের বহর।
এই সময়ে তিনি সন্ধান পেলেন মক্কার আর এক বুজুর্গ ব্যক্তি। তাঁর নাম মাওলানা তাহের চোম্বল।
মক্কায় তিনি ছোটো আবু হানিফা নামে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।
হাজী শরীয়তুল্লাহ এই বুজুর্গ আলেমে দীন- মাওলানা তাহের চোম্বলের কাছে প্রায়ই যেতেন।
মাওলানা তাহের মক্কায় একজন আধ্যাত্মিক পণ্ডিত ও সংস্কারক হিসাবেও পরিচিত ছিলেন।
তাঁর চরিত্র মাধর্যে এবং তা৭র শিক্ষা ও সংস্কারে মুগ্ধ হয়ে হাজী শরীয়তুল্লাহও তাঁকে অনুসরণ করেন।
মক্কায় বিশ বছর ছিলেন হাজী শরীয়তুল্লাহ। এ সময়ের মধ্যে তিনি একাধিক হজ পালন করেন।
স্বদেশের দিকে
মক্কা বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা দান এবং মাওলানা তাহের চোম্বলের কাছে ইসলাম ও আত্মশুদ্ধি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে থাকেন হাজী শরীয়তুল্লাহ।
কিন্তু স্বদেশে ফেরার জন্যে তাঁর হৃদয়টা ব্যাকুলতা হয়ে উঠলো।
কেবলই মনে পড়তে থাকলো তাঁর আপন মাতৃভূমির কথা। স্বজনদের কথা। প্রিয় চাচার কথা।
চাচা মুহাম্মদ আজিমের অসুস্থতার খবরও তিনি পেয়ে গেছেন।
এসব কথা ভাবতে গিয়ে মক্কার প্রবাস জীবনে অস্থির হয়ে ওঠেন হাজী শরীয়তুল্লাহ।
সিদ্ধান্ত নেন মক্কা থেকে স্বদেশে ফিরে আসার।
অবশেষে তিনি ফিরে এলেন স্বদেশের মাটিতে। সময়টা ছিলো আঠারো শো আঠারো সাল।
হাজী শরীয়তুল্লাহ দীর্ঘ প্রবাস জীবন শেষে যখন নিজ গ্রাম শামাইলে পৌছুলেন,তখন দেখলেন তাঁর একমাত্র জীবিত চাচা মুহাম্মদ আজিম তালুকদার ভীষণ অসুস্থ।
প্রাণ-প্রিয় চাচার এই করুণ অবস্থা দেখে ডুকরে কেঁদে উঠলেন হাজী শরীয়তুল্লাহ!
চারদিকে আঁধার কালো
খুব শৈশবে গ্রাম ছেড়েছিলেন শরীয়তুল্লাহ।
তিনি মক্কা থেকে ফিরে এসে তখনকার সেই পরিচিত মুখগুলোর মধ্যে অনেককেই আর দেখতে পেলেন না!
এর মধ্যে হারিয়ে গেছে তাঁর কত যে চেনা মুখ! কত যে কাছে মানুষ! কত যে খেলার সাথী!
স্বজন হারানোর এই বেদনা হাজী শরীয়তুল্লাহকে খুব ব্যথিত করে তুললো। কিন্তু তার চেয়েও তিনি বেশি ব্যথিত হলেন চার পাশের মানুষ ও তাদের পরিবেশ দেখে।
আতকে উঠলেন তাদের অধঃপতন দেখে!
কুসংস্কার, অশিক্ষা, কুশিক্ষা, অভাব দারিদ্র আর শোষণ নির্যাতনে মুষড়ে পড়া মুসলিম পরিবারগুলোর দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারেন না
হাজী শরীয়তুল্লাহ!
চারদিকে আঁধারের কালো ছায়া!
এদেশে তখনো ইংরেজদের দখলে।
ইংরেজদের শোষণ আর অত্যাচারে অতিষ্ট শহরের মানুষ। তার চেয়েও বেশি অতিষ্ট গ্রামের মানুষ।
পাড়া-গ্রামে চলছে অত্যাচারী জমিদার, মহাজন আর নীল করদের একচেটিয়া দাপট।
শুধু ইংরেজই নয়।
এদেশের হিন্দু জমিদাররাও তাদের সাথে মিশে অত্যাচারের বিষে জর্জরিত করছে সাধারণ মুসলমানকে।
সে সময়ে গ্রামের অধিকাংশ মুসলমানই ছিলো অত্যন্ত দরিদ্র।
তাদেরকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে দিতো না একদিকে ইংরেজ, নীলকর এবং অপরদিকে এ দেশীয় হিন্দু এবং হিন্দু মহাজন ও জমিদাররা। অসহায় দরিদ্র মুসলমানদের অধিকাংশই ছিলো অশিক্ষিত।
একটু যারা শিক্ষিত তারাও ছিলো অনেকটা অসচেতন। ইংরেজরা হিন্দু ও হিন্দু জমিদারকে খুব সুনজরে দেখতো। হিন্দুদেরকে তারা খুব কদর করতো। আর মুসলমানরা ছিলেঅ তাদের দু’চোখের বিষ।
তারা মুসলমানদেরকে শত্রু ভাবতো।
তাই তারা সুকৌশলে সকল সময় হিন্দুদেরকে ক্ষেপিয়ে তুলতো দরিদ্র অশিক্ষিত মুসলমানদের ওপর।
ইংরেজদের আশকারা আর মদদ পেয়ে হিন্দুরা ছলে-বলে-কৌশলে মুসলমানদের গ্রাস করতে উদ্যত হতো।
তারা গ্রাস করতো মুসলমানদের অর্থ-সম্পদ, জমি-জায়গা।
তাতেও তারা খুশি হতো না।
এরপর তারা মুসলমানদের ধর্মীয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক দিক দিয়েও ধ্বংস করার চেষ্টা করতো সর্বক্ষণ।
মুসলমানদের ইসলাম থেকে, তাদের ঐতিহ্য থেকে দূরে রাখার সকল প্রকার অপকৌশল প্রয়োগ করতো হিন্দুরা।
তাদের হাতে ক্ষমতা আর অর্থ থাকার কারণে তারা সহজেই প্রভাবিত করতে পারতো দরিদ্র-অশিক্ষিত মুসলমানদেরকে।
এইভাবে এক সময় মুসলমানরা কুসংস্কারের অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে পড়লো। হাজী শরীয়তুল্লাহ দেখলেন মুসলমানদের এই করুণ পারিবারিক ও সামাজিক অবস্থা।
তিনি দেখলেন, মুসলমানরা রোযা-নামাযসহ আল্লাহর ইবাদাত ছেড়ে দিয়ে, আপন সংস্কৃতি ভুলে গিয়ে হিন্দুদের সংস্কৃতিকে গ্রহণ করে নিয়েছে!
তারা নামেই কেবল মুসলমান আছে।
তাদের মধ্যে নেই ইসলামের কোনো ছায়া চিহ্ন।
ইসলামের কোনো কিছুই তারা পালন করে না।
দীর্ঘকাল হিন্দুদের দ্বারা প্রভাবিত হবার কারণে হিন্দুয়ানী আচার অনুষ্ঠান ও হিন্দু সংস্কৃতিতে তারা গা ভাসিয়ে দিয়েছে।
ইসলারেম যে মৌলিক ও পৃথক সংস্কৃতি বলে কিছু আছে- এ কথাও তারা ভুলে গেছে।
কি সর্বনাশে ব্যাপার!
তাদের এই অধঃপতন দেখে খুবই মর্মামহত হলেন হাজী শরীয়তুল্লাহ।
তিনি পথভোলা মানুষের কাছে নতুন করে ইসলামের দাওয়াত দেবার প্রয়োজনবোধ করলেন। এই বোধ থেকেই তিনি শুরু করলেন ইসলামের দাওয়াতী তৎপরতা।
বেদগান করলেন তাঁর সংস্কার আন্দোলন।
মানুষকে আহ্বান জানান তিনি সত্যের দিকে। আল্লাহর দিকে।
সাধারণ মুসলমানকে তিনি বুঝান ইসলারেম আকীদা-বিশ্বাস।
বুঝান ইসলামের সুমহান আদর্শ ঐতিহ্য।
বুঝান সত্য আর মিথ্যার পার্থক্য।
কিন্তু কি আফসোস!
গ্রামের মুসলমানরা এতোটাই অন্ধকারে ডুবেছিলো যে, হাজী শরীয়তুল্লাহর শত আহ্বানেও তারা প্রথমত এতোটুকু সাড়া দেয়নি।
তারা চিনতে ভুল করলো সত্য-সঠিক পথ। বুঝতে ভুল করলো হাজী শরীয়তুল্লাহকে।
অন্ধ মানুষের মধ্যে দীনের দাওয়াত দিতে গিয়ে প্রথম দিকেই ব্যর্থ হলেন হাজী শরীয়তুল্লাহ।
তাদের গুমরাহীতে ভীষণ কষ্ট পেলেন তিনি।
ভেবেছিলেন, অন্ধকারাচ্ছন্ন-পথভোলা গ্রামের আপন মানুষকে তিনি পথের দিশা দেখাবেন।
তাদেরকে আবার ইসলামের আলোয় আলোকিত করবেন। কিন্তু পারলেন না তিনি।
পারলেন না হাজী শরীয়তুল্লাহ।
কারণ তাঁর কথা কেউ শুনলো না।
আবারো মক্কার পথে
আপন গ্রামের মানুষকে সত্যের পথে ডেকে যখন তাদের কোনো সাড়া পেলেন না, তখন কিছুটা হতাশ হয়ে আবারো মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করলেন হাজী শরীয়তুল্লাহ।
বুকে তাঁর ব্যর্থতার যন্ত্রণা! কষ্টের তুফান! কোনো যানবাহনে নয়।
এবার চললেন তিনি সম্পূর্ণ পায়ে হেঁটে।
মক্কায় যাবার পথে প্রথমে তিনি বাগদাদে গেলেন।
বাগদাদে ঘুমিয়ে আছেন বহু শহীদ, গাজী, পীর-দরবেশ, আলেম-উলামা এবং অজস্র নেক ব্যীক্ত।
হাজী শরীয়তুল্লাহ সেই সকল পবিত্র কবর যিয়ারত করেন। যিয়ারত করেন যারা দীনের জন্যে, ইসলামের জন্যে নিজেদের জীবনকে কুরবানী করে ঘুমিয়ে পড়েছেন গহীন কবরে।
এই সকল কবরের মধ্যে আছে দয়ার নবীজীর (সা) কলিজার টুকরা, নয়নের মণি নাতি- হযরত হুসাইনের (রা) পবিত্র কবরও।
দীনের জন্যে আত্মত্যাগের এক বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী ইমাম হোসাইনের (রা) স্মৃতি-বিজড়িত কারবালা প্রান্তরে ইমামের শাহাদাতগাহ, তাঁর কবর এবং আবদুল কাজের জিলানীর (র) কবরও যিয়ারত করেন হাজী শরীয়তুল্লাহ।
তিনি ঘুরে ঘুরে বিখ্যাত সকল ব্যীক্তর কবর যিয়ারত করলেন।
এরপর তিনি বাইতুল মাকদিস ও মিসর সফর শেষে পৌঁছে যান পবিত্র মক্কায়। মক্কায় পৌঁছে হাজী শরীয়তুল্লাহ পুনরায় খোঁজ করেন তাঁর প্রিয় শিক্ষক মাওলানা তাহের আলীকে।
তাঁর সাথে সাক্ষাতের পর হাজী শরীয়তুল্লাহ আবারো হজ পালন করেন। তারপর রওয়ানা হলেন মদীনার পথে।
হাজী শরীয়তুল্লাহ এবার মাত্র দু’বছর থাকেন মক্কায়ে।
সেখানে থাকাকালীন সময়ে তিনি গভীরভাবে ইসলামের খুঁটিনাটি বিষয়সমূহ ছাড়াও আধ্যাত্মিক সাধনায় নিজেকে ব্যস্ত রাখেন।
তিনি মদীনায় গিয়ে নবীজীর (স) কবর মুবারক যিয়ারত করেন।
রাসূলের (সা) পবিত্র রওজযা মুবারকে দাঁড়িয়ে হাজী শরীয়তুল্লাহ স্বদেশের মুসলমানদের বিপর্যয়ের কথা স্মরণ করে তাদের মুক্তি ও হিদায়েতের জন্যে বিশেষভাবে দোয়াও করলেন।
সেখানে অবস্থানকালে তিনি একে একে তিনবার প্রাণ-প্রিয় রাসূলুল্লাহকে (সা) স্বপ্নে দেখেন।
রাসুল (সা) প্রতিবারেই তাঁকে দেশে ফিরে ইসলাম প্রচারের নির্দেশদেন। এই আশ্চর্যজনক স্বপ্নের কথা হাজী শরীয়তুল্লাহ খুলে বললেণ তাঁর মক্কার শিক্ষক মওলানা তাহের আলীকে।
বিজ্ঞ আলেমে দ্বীন মাওলানা তাহের আলী সকল কথা শুনে হাজী শরীয়তুল্লাহকে একজন সৌভাগ্যবান ব্যক্তি বলে অভিহিত করলেন।
তারপর তাঁকে বললেণ, স্বদেশে ফিরে ইসলাম প্রচারের কাজে আত্মনিয়োগ করতে।
দু’বছর মক্কা ও মদীনা সফর করার পর হাজী শরীয়তুল্লাহ আবারো রওয়ানা দিলেন স্বদেশের পথে।
সালটি ছিলো আঠারো শো বিশ।
আল্লাহর কি অপার মহিমা!
হাজী শরীয়তুল্লাহ এবার দেশে ফিরে দেখেন অন্য অবস্থা!
ভিন্ন এক পরিবেশ!
তিনি দেখেন চারদিকে জেগে উঠেছে মজলুম জনতা।
আন্দোলন এবং সংগ্রামের ঝড় উঠেছে হিন্দু জমিদার এবং ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে।
এসব দেখে তিনি অত্যন্ত খুশী হলেন। আর তাঁর দোয়া কবুল হবার জন্য শুকরিয়া জানালেন মহান রাব্বুল আলামীনকে।
হাজী শরীয়তুল্লাহর বুকে আরও প্রচণ্ড বেগে শুরু হলো সেই ঝড়ের তোলপাড়!
বারবার লড়ে যায় বীর
বারো শো তিন সাল থেকে সাড়ে পাঁচশো বছর পর্যন্ত বছর পর্যন্ত মুসলমানরা বাংলার শাসন পরিচালনা করেছিলেন।
অবশেষে এলো সতেরো সাতান্ন সাল।
পলাশীর যুদ্ধে পরাজিত হলেন বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদ্দৌলাহ। এই যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে ইংরেজরা কেড়ে নিলো মুসলমানের হাত থেকে বাংলাদেশের শাসন ক্ষমতা।
কেড়ে নিলো তারা জনগণের সকল স্বাধীনতা।
ইংরেজ শাসনের সময় হিন্দুরা ছিলো তাদের অনুগত দাসানুদাস।
আর মুসলমানা ছিলো বিদ্রোহী।
পলাশীর যুদ্ধে পরাজয় বরণ করে মুসলমানরা কেবল রাজ্যই হারালেনা, তারা হারালো সর্বস্ব।
একদিন যে মুসলমানের হাঁক-ডাকে সরব হয়ে উঠতো চারদিক, মুহূর্তেই থেমে গেলা তাদের সেই তুমুল গর্জন।
একদিন যে মুসলমানের জন্যে দরিদ্র কিংবা নিঃস্ব হওয়া চিলো প্রায় অসম্ভব, ইংরেজরা ক্ষমতা দখলের পরপরই সেই মুসলমানরা পরিণত হলো কাঠুরিয়া এবং ভিস্তিওয়ালায়।
লাঞ্চিত এবং বঞ্চি হতে থাকলো তারা নির্মমভাবে।
মীর জাফরের মতো গুটিকয়েক অপরিণামদর্শী। উচ্চাভিলাষী নামদারী মুসলমান ইংরেজ ও হিন্দুদের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে বেপথু হয়ে সিরাজদ্দৌলাহকে পলাশীতে বিপর্যয়ের মধ্যে ফেলে দিলো।
সেকান থেকেই মুসলমানের ভাগ্যে অংকিত হয়ে গেলো অপমমান আর লাঞ্ছনার কালো চিহ্ন।
তবুও সংগ্রাম থেমে থাকেনি একটি মুহূর্তের জন্যেও। কেনই বা থামবে?
মুসলমানদের রক্তে মিছে আছে ঈমান আর অসীম সাহসের বারুদ! প্রয়োজনে তারা জ্বলে ওঠে বারবার। গর্জে ওঠে সিংহরে মতো। যেমন গর্জে উঠেছিলো সেদিন অনেকেই। ইংরেজদের দুঃশাসন আর হিন্দুদের অত্যাচার থেকে এই দেশকে মুক্ত করার জন্যে, এই জাতিকে রক্ষা করার জন্যে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো সময়ের সাহসী পুরুষেরা।
আবারো জেগে উঠলো তাদের সাথে মুসলমান।
তাদের সংগ্রামকে প্রতিহত করার জন্যে হিন্দুদের সহযোগিতায় ইংরেজরাও তৎপর হয়ে উঠলো।
মুসলমানদের ওপর তারা চালাতে শুরু করলো অকথ্য জুলুম আর নির্যাতনের স্টিম রোলার।
তবুও থেমে থাকলো না সংগ্রামের দাবানল!
সতেরো শো চৌষট্টি সাল।
বিদ্রোহী নবাব মীর কাসিম বাংলার স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের জন্যে প্রত্যক্ষ যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।
কিন্তু বক্সারের যুদ্ধে তিনি পরাজিত হলেন চরমভাবে। ব্যর্থ হলো প্রাণ-প্রিয় বাংলঅকে রক্ষা করার তাঁর সর্বশেষ প্রচেষ্টাও।
বক্সারের যুদ্ধের পূর্বেই জেগে উঠেছিলো এদেশের আর এক বিদ্রোহী গোষ্ঠী। ‘ফকির বিদ্রোহ’ নামে খ্যাত এই বিদ্রোহী গোষ্ঠীতে ছিলেন সেই যুগের বহু পীর, ফকির ও অসংখ্য আলেম।
এই বিদ্রোহের নাম ছিল ‘ফকির বিদ্রোহ’।
ফকির বিদ্রোহের নেতা ছিলেন দুঃসাসী এক লড়াকু সৈনিক মজনু শাহ।
সতেরো শো তেষট্টি সাল।
ফকির বিদ্রোহীরা আকস্মিকভাবে আক্রণ করলেন বাকেরগঞ্জ ইংরেজ কোম্পানীর কুঠি।
তাঁরা মীর কাসিমের বাহিনীতেও যোগ দিয়েছিলেন।
তাঁরা সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিলেন ইংরেজদের বিরুদ্ধে। ফকির বিদ্রোহীদের নেতা মজনু শাহরে মৃত্যুর পর মুসা শাহ, চেরাগ আলী, সোবহান শাহ, মাদার বকশ, করিম শাহ প্রমুখ ফকির নেতা এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন।
তাঁদের সংগ্রাম ছিলো মূলত ইংরেজদের বিরুদ্ধে।
এই বিদ্রোহের ফলে ইংরেজ কোম্পানীর সৈন্যদের সাথে তাঁদের অনেক যুদ্ধ হয়েছে।
অনেক সংঘর্ষ হয়েছে।
কিন্তু তারা এতোটুকুও পিছু হটেননি। বরং বাংলাদেশের উত্তর অঞ্চলের একটি বিশাল এলাকা জুড়ে তাঁরা ইংরেজদেরকে কাঁপিয়ে তুলেছিলেন।
তাঁদের সেই সংগ্রামের কথা আজো ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা রয়েছে।
আঠারো শো ছাব্বিশ সাল।
ফকির বিদ্রোহ যখন একটু ঝিমিয়ে পড়েছে তখনই গর্জে উঠলেন আর এক সাহসী সৈনিক- সৈয়দ আহমদ শঞীদ!
তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে, অত্যাচারী শিখ রাজার বিরুদ্ধে এক মহা বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন।
তাঁর আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিলো মুসলমানদের আল কুরআন ও আল হাদীসের শিক্ষায় পূর্ণভাবে ফিরে আনা এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের সময়ের মতো ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা।
মুসলমানদের স্বাধীনতা এবং ইসলামের আদর্শ ও ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠায়ও এই আন্দোলনের বিশেষ ভূমিকা ছিলো।
এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে সৈয়দ আহমদ শহীদ তাঁর আন্দোলনকে বেগবান করে তুলেচিলেন বাঁধভাঙ্গা স্রোতেরমতো।
আফগান সীমান্তের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ঘাঁটি গেড়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে মুসলমানরা শুরু করলো মুক্তির সংগ্রাম।
আঠারো শো ছাব্বশ সালে ইংরেজ-মিত শিখদের সাথে তাদের প্রথম যুদ্ধ হলো।
ভয়ংকর এক যুদ্ধ!
সৈয়দ আহমদ শহীদ এই প্রত্যক্ষ সংগ্রাম শুরুর প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিলেন প্রায় এক দশক আগে।
বাংলাদেশসহ গোটা ভারত সফর করে তিনি সকল মুসলমাকে জাগিয়ে তুলেছিলেন।
আছারো শো একত্রিশ সাল।
এই বিদ্রোহের নায়ক সৈয়দ আহমদ বেরেলভী বালাকোটে শাহাদাত বরণ করলেন।
বিশ্বাসঘাতকদের শিকার হয়ে তিনি এবংতাঁর শীর্ষস্থানীয় সাথীরা শাহাদাত বরণ করেছিলেন।
বালাকোটে যারা শাহাদাত বরণ করেন তাঁদের মধ্যে নয়জন বাংলাদেশীর নাম পাওয়া যায়।
আহতদের মধ্যে ছিলেন আরও চল্লিশ জন।
নারকেল বাড়িয়ার রণাঙ্গনে পরাজয় ও শাহাদাত বরণ করেন বাংলার আরেক সিংহ পুরুষ, দুঃসাহসী- সেনাপতি সাইয়েদ নিসার আলী তিতুমীর!
সেটিও ছিলো আঠারো শো একত্রিশ সাল।
মহা বিস্ময়েরই ব্যাপার বটে!
এই সংগঠন আঠারো শো ছাব্বিশ সাল থেকে আঠারো শো আটষট্টি সাল- এই দীর্ঘকাল যাবত ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে চলেছিলো।
এই সকল আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় যুক্ত হলেন আর একজন সংগ্রামী পুরুষ।
আর একজন সাহসী বীর।
তাঁর নাম- হাজী শরীয়তুল্লাহ!
গর্জে উঠলেন সাহসী সৈনিক
মুসলমানদের অধঃপতন দেখে আঁতকে উঠলেন হাজী শরীয়তুল্লাহ!
অন্ধকার থেকে তাদের আলোর পথে তুলে আনবার জন্যে তিনি ব্যাপকভাবে দীনি দাওয়াতের কাজ শুরু করলেন।
যাবতীয় কুসংস্কার আন্দোলন চালাতে থাকলেন।
সাধারণ মুসলমানকে নৈতিক শিক্ষায় তিনি উদ্বুদ্ধ করে তোলেন। অপরদিকে তিন ইংরেজ এবং অত্যাচারী জমিদার হিন্দুদের বিরুদ্ধেও রুখে দাঁড়ালেন।
তারা ক্ষেপেগেল ভীষণভাবে হাজী শরীয়তুল্লাহর প্রতি।
তবও তাদের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে গর্জে উঠলেন সাহসী সৈনিক- হাজী শরীয়তুল্লাহ
দীর্ঘকাল মক্কায় থেকে হাজী শরীয়তুল্লাহ কেবল কুরআন, হাদীস, ফিকাহ, তাসাউফই শেখেননি, তিনি বিশেষ জ্ঞান অর্জন করেছিলেন ইসলাম, সমাজ বিজ্ঞান ও রাজনীতি সম্পর্কেও।
এ সময়ে তিনি বুঝলেন, ইসলাম কেবল একটি ধর্মের নাম মাত্র নয় বরং একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থার নাম- ইসলাম।
ইসলামের বিস্তারিত ব্যাখ্যা সম্পর্কে অবহিত হবার পর এর প্রচার এবং প্রসারের জন্যে হাজী শরীয়তুল্লাহ নতুনভাবে উদ্যোগী হলেন।
এক মহা আত্ম-প্রত্যয়ের সাথে তিনি নিজের পথকে আবিষ্কার করলেন। আত্মত্যাগ ও আত্মকুরবানীর শিক্ষায় উজ্জীবিত হয়ে তিনি ইসলামের দাওয়াতের কাজ শুরু করলেন ব্যাপকভাবে।
এই দাওয়াতী কাজ শুরু করলেন তিনি তাঁর স্বগ্রামে। স্বদেশে।
আপন-পর-সকল মানুষের মাঝে।
কিন্তু কাজটি ছিলেঅ না খুব সহজসাধ্য। কেননা তখনো তাঁর চারপাশে অশিক্ষা, কুশিক্ষা এবং অপসংস্কৃতির পংকিলে হাবুডুবু খাচ্ছিলো সাধারণ মুসলমান।
তখনকার সামাজিক অবস্থাটা ছিলো অত্যন্ত বেদনাদায়ক।
একদিকে চলছে ধর্মীয় অনাচার, অন্যদিকে রাজনৈতিক অস্থিরতা। আর আছে সাধারণ মুসলমানদের ঘাড়ের ওপর ইংরেজ দস্যু, নীলকর ও অত্যঅচারী হিন্দু জমিদারদের ক্ষিপ্ত শাণিত চাবুক!
আচেতাদের হাতে চকচকে ক্ষুরধার তরবারি!
এর মধ্যে দিয়েই হাজী শরীয়তুল্লাহ নতুনভাবে, নতুন উদ্যমে ঝড়ের মতো এগিয়ে চললেন সামনে।
ক্রমাগত।
ফরায়েজী আন্দোলন
সতেরো শো চৌষট্টি সাল।
মীর কাসিমকে পরাজিত করলো ইংরেজরা।
এরপর থেকে তারা মুসলমানদের ওপর জুলুম-নির্যাতনের মাত্রা আরো বাড়িয়ে দিলো অনেকগুণে।
ইংরেজরা মুসলমানদেরকে সকল দিক দিয়ে ধ্বংস এবং নির্মূল করার জন্যে নানা ধরনের অপকৌশলের আশ্রয় নিলো!
মেতে উঠলো তারা ঘৃণ্য-কুটিল ষড়যন্ত্রে।
ইংরেজরা আক্রমণ করলো মুসলমানদের ধর্ম ও সংস্কৃতির ওপর। তাদের অর্থনীতির ওপর।
মুলমানদের আয়মা, লাখেরাজ বাজেয়াপ্ত হলো।
তাদের হাত থেকে খাজনা আদায়েল ভার ছিনিয়ে নিয়ে তা দিয়ে দিলে অনুগত হিন্দুদের হাতে।
আর এই সুযোগ পেয়ে চরম সাম্প্রদায়িক হিন্দুরা আনন্দে লাফিয়ে উঠলো। বহুদিন যাবত তারাও ওঁৎ পেতে ছিলো সুযোগের অপেক্ষায়।
এমনি একট মোক্ষম অস্ত্রের খোঁজ করছিলো তারা বহুদিন থেকে- যা দিয়ে বহুকালের শত্রু- মুসলমানদেরকে তারা আরো বেশি করে শায়েস্তা করতে পারে।
খাজনা আদায়ের দায়িত্ব পেয়ে হিন্দুরা বিপুল বেগে চড়াও হলো মুসলমানদের ওপর। ইংরেজদের সরাসরি মদদ পেয়ে তাদের সাহসের মাত্রা বেড়ে গেলো হাজার গুণে।
খাজনা আদায়ের অজুহাতে কারণে-অকারণে তারা মুসলমানদের ওপর অত্যাচার নিপীড়ন চালাতে থাকলো অত্যন্ত নির্মমভাবে।
কি ভয়ানক ছিল তাদের সেই অত্যাচার আর নিপীড়ন!
তাদের সেই নির্মম নিষ্ঠুরতার ইতিহাস আলোচনা করতে গেলে এখনো শরীর শিউরে ওঠে!
ভয়ে এবং আতংক কেঁপে ওঠে বুক।
মুসলমানদের অর্থ-সম্পদ, জমি জায়গা ছলে বলে দখল করেও তৃপ্ত হতো না হিন্দুরা।
শারীরিকভাবেও তারা নির্যাতন চালাতো তাদের ওপর।
আর মুসলমানদের ধর্মীয় কাজে বাধা সৃষ্টি করা ছিলো তাদের অন্যতম প্রধান কাজ।
অত্যাচারী হিন্দু জমিদারদের এলাকায় কোনো মুসলমান গরু কিংবা পশু কুরবানী দিতে পারতো না।
দিতে পারতো না মসজিদে আযান।
এমনকি ইসলারেম অন্যান্য হুকুম-আহকামও পালন করতে পারতো না স্বাধীনভাবে।
মুসলমানদের সকল ক্ষেত্রেই বাধা দিতো হিন্দু জমিদাররা।
জমিদারদের সাথে থাকতো পশু স্বভাপের হিংস্র লাঠিয়াল বাহিন।
তারা মুসলমানদের ওপর যখন ঝাঁপিয়ে পড়তো বাঘের মতো।
কি জঘন্য এবং মর্মান্তিক বিষয়!
হিন্দু জমিদাররা এ সময়ে মুসলমানদের দাড়ির ওপরও ট্যাক্স বসিয়ে দিলো!
তাদের ধূতি পরতে বাধ্য করা হতো!
দাড়ি কেটে গোঁফ রাখতে নির্দেশ দিতো!
আর পূজার সময়ে মুসলমানদের কাছ থেকে জোরপূর্বক আদায় করতো চাঁদা, ছাগল, হাঁস-মুরগিসহ পূজার আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র!
এছাড়াও তারা গরীব মুসলমানদের পূজার সময়ে খাটিয়ে নিতো বিনা পারিশ্রমিকে।
যারা তাদের অবাধ্য হতো তাদের ওপর চালাতো নির্মম নির্যাতন।
এভাবেই মুসলমানরা অর্থ এবং ধর্ম হারিয়ে হিন্দুদের হাতে জিম্মি হয়ে পড়েছিলো।
মুসলমানদের ঠিক এই চরম দুঃসময়ে মক্কা থেকে ফিরে এলেন আপন স্বদেশে হাজী শরীয়তুল্লাহ।
তিনি স্বদেশের বুকে পা রেখেই আঁতকে উঠলেন!
চারদিকে তাকিয়ে দেখলেন অবাক বিস্ময়ে!
কেঁপে উঠলো তাঁর দরদ ভরা বুক!
দেখলেন হিন্দু-মুসলমানের আচার আচরণ।
তাদের এই আচার আচরণের মধ্যে খুঁজে পেলেন না হিন্দু মুসলমানের মৌলিক পার্থক্যকারী ইসলামের সেই মহান আদর্শ এবং শিক্ষা।
ইসলামের চর্চা নেই ব্যক্তি কিংবা সমাজ জীবনের কোথাও।
মুসলমানদের কাছে তিনি শুনলেন তাদের সকল দুর্ভাগ্যের কথা।
শুনলেন ইংরেজ এবং হিন্দদের অত্যচারের কথা।
নিজের চোখেও দেখলেন অনেক কিছু।
এসব দেখে আর শুনে ব্যথিত হলেন হাজী শরীয়তুল্লাহ!
ভাগ্যহত মুসলমানদের অন্ধকারের কালো গুহা থেকে টেনে তুলবার জন্যে তিনি সংকল্পবদ্ধ হলেন কঠিনভাবে।
আর তখনই হিন্দু ও ইংরেজদের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠে তাঁর সাহসী কণ্ঠ!
শুরু হলো তাঁর দেশ, জাতি ও ইসলামী আদর্শ-ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারের দুর্বার সংগ্রাম!
সংস্কারের এক কঠিন সংগ্রাম!
হাজী শরীয়তুল্লাহর এই সংগ্রামের নাম, এই আন্দোলনের নাম-‘ফরায়েজী আন্দোলন।’
‘ফরজ’ থেকে ‘ফরায়েজী’। ফরায়েজ শব্দটি বহুবচন।
ফরিজাহ শব্দের অর্থ দাঁড়ায় আলআহর নির্দেশিত অবশ্য কর্তব্যসমূহ। যারা এই কর্তব্যসমূহ পালনে অংগীকারাবদ্ধ তাদেরকে ‘ফরায়েজী’ বলা হয়।
হাজী শরীয়তুল্লাহ সকল আরাম আয়েশ ত্যাগ করে গ্রাম থেকে গ্রামে, শহর থেকেশহরে ঘুড়ে বেড়ান।
এভাবে ঘুরে ঘুরে তিনি সংগ্রহ করেন আপন সংগঠনের জন্যে নিবেদিত কর্মী। সক্রিয় সদস্য।
হাজী শরীয়তুল্লাহ এই আন্দোলনের আগুনকে ছড়িয়ে দেন চারদিকে।
যারা ইসলামের ফরজসমূহ পালন করতে রাজি তারাই কেবল ফরায়েজী আন্দোলনের সদস্য হতে পারতো।
খুব অল্প সময়ের মধ্যে তিনি বিপুল সংখ্যক মুসলমানকে এই আন্দোলনের সদস্য করে তুলেছিলেন।
হাজী শরীয়তুল্লাহ তাঁর সদস্য এবং সাধারণ মুসলমানকে ধর্মের সাথে কর্মের মিল রাখার জন্যে কঠোরভাবে নির্দেশ দিলেন।
আল্লাহর হুকুম-আহকাম মেনে চলার জন্যে তিনি সকলের প্রতি আহ্বান জানালেন। আহ্বান জানালেন শিরক, কুফরী ও বিদআত থেকে দূরে থাকতে।
ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতির আলোকে নিজের জীবনযাত্রা পরিচালনা ও আচার অনুষ্ঠান পালন করার জন্যে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করলেন।
হাজী শরীয়তুল্লাহর আন্দোলন সম্পর্কে জেমস টেইলর বলেন, যে “কুরআনকে অক্ষরে অক্ষরে পালন করাই ছিলো ফরায়েজী আন্দোলনের উদ্দেশ্য।
কুরআন যেসব অনুষ্ঠানাদি সমর্থন করে না তা সবই ছিলো বর্জনীয়।
মহররমের অনুষ্ঠান পালনই শুধু নিষিদ্ধ ছিলো না, এ অনুষ্ঠানের ক্রিয়াকলাপ দেখাও ছিলো তাদের জন্যে নিষিদ্ধ।”
যেখানে পশু কুরবানী দেয়াই ছিল, সেখানে হিন্দুদের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে হাজী শরীয়তুল্লাহ নিজেই গরু কুরবানী দিলেন।
সবাই অবাক- বিস্ময়ে দেখলো হাজী শরীয়তুল্লাহর সাহস।
তাঁর এই সাহসে অন্য মুসলমানও উদ্বুদ্ধ হলো।
এরপর তিনি অন্যান্য মুসলমানকেও গরু কুরবানী দিতে বললেন।
দাড়ির ওপর ট্যাক্স দিতেও মুসলমানদেরকে কঠোরভাবে নিষেধ করলেন। আর শক্তভাবে নিষেধ করলেন হিন্দুদের পূজা পার্বণে চাঁদা বা পশু পাখি দিতে। হিন্দু জমিদারদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে তিনি আরো বেশী সোচ্চার হলেন। চারকিকে শুরু হয়ে গেলো তুমুল আন্দোলন!
হাজী শরীয়তুল্লাহর এই সাহসী আন্দোলন ছিলো সত্যের পক্ষে আর অন্যায়ের বিরুদ্ধে।
হাজী শরীয়তুল্লাহর এই সাহসীকর্ম তৎপরতায় ক্ষেপে গেলো অত্যাচারী হিন্দুরা।
ক্ষেপে গেলো হিন্দু জমিদার এবং ইংরেজরাও।
চারদিকে শুরু হয়ে গেলো সংঘর্ষ!
সংঘর্ষ হলো তাদের জায়গায়!
কিন্তু পিছু হটলো না ফরায়েজীর সিংহদিল কর্মীরা!
যতোই বাধা আসতে থাকলো, ততোই বিদ্যুৎগতিতে ছড়িয়ে পড়তে থাকলো ফরায়েজী আন্দোলনের তীব্র আগুন।
শত বাধার মুখেও হাজী শরীয়তুল্লাহ ছিলেন অনড় এক পর্বত!
আর তাঁর সাথীরাও ছিলো তেমনি সত্যের পথের এক একজন সিংহপুরুষ!
হাজী শরীয়তুল্লাহ ছিলেন হানাফী মাজহাবের অনুসারী এবং সেই সাথে বাংলাভাষী।
পারিবারিকভাবে ক্ষুদ্র তালুকদার হলেও শেষ পর্যন্ত সেটাও ছিল না।
তিনি যখন হজ পালন করে বাড়ি ফেরেন, তখন তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা তেমন ভাল ছিল না।
অন্যদিকে মুসলমান সমাজের উঁচু দরের বা আশরাফ হিসেবেও পরিচিত ছিলেন না।
তাতে কি
তবুও মধ্যম গড়নের, দীর্ঘ দাড়ি সম্বলিত হাজী শরীয়তুল্লাহ ছিলেন বাঙালি মুসলমানের জন্য প্রকৃত ইসলামী সমাজ সংস্কারের একজন রূপকার।
তাই সাধারণ মানুষের মাছে তাঁর মিশে যাওয়া খুব অসুবিধা হয়নি। বরং সাধারণ মানুষ তাঁর বুকে ঠাঁই পেয়েছে। পেয়েছে মাঝে একজন আপন লোক। তার ওপর তিনি ইসলামের পুণ্যভূমি মক্কায় দীর্ঘদিন অবস্থান করে অনেক কিছু শিখেছেন। তাঁর সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন চরিত্র সাদামাঠা জীবন অমায়িক ব্যবহার, আন্তরিক, প্রয়াস, সবাইকে সমান মর্যাদা প্রদানের অঙ্গীকার- যে কাউকে মোহিত ও মুগ্ধ করার জন্য ছিল যথেষ্ট।
এমন একজন অনুকরণ ও অনুসরণযোগ্য নেতাই তখনকার পরিবেশে প্রয়োজন ছিল অনেক বেশী।
সাধারণ মানুষের সমস্যা তিনি বুঝতেন এবং কিভাবে তার সমাধান করা যায়, তাও জানা ছিল তাঁর। ফলে তিনি সহজেই একটি গতিশীল আন্দোলন সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন।
ফলে সেই সময়ে অনেক আন্দোলন সৃষ্টি হলেও ফরায়েজী আন্দোলনই হয়ে উঠেছিল সবচেয়ে কার্যকর, ফলপ্রসূ এবং স্থায়ী।
ইংরেজ সিভিলিয়ন জেম টেলর তা ‘A Sketch of the Topography and statistics of Dacca’ তে লিখেছেন,
“১৮২৮ সালের পর থেকে ফরায়েজী আন্দোলন ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত হচ্ছে।”
অন্যদিকে জেমস ওয়াইজের মতে,
“শিরক ও বিদআত থেকে স্থানীয় মুসলমানদের রক্ষা করার ক্ষেত্রে হাজী শরীয়তুল্লাহই পূর্ববঙ্গের ইসলামের প্রথম সংস্কারক ও প্রচারক।”
সুতরাং এ থেকেই বুঝা যায়, ইসলামের জন্য হাজী শরীয়তুল্লাহর অবদানটা কত বেশী!
একজন অভিভাবকের কথা
হাজী শরীয়তুল্লাহ বাংলার মুসলিম সমাজে একজন অভিভাবকের ভূমিকা পালন করতেন।
বিপদে মুসিবতে, সুখে-দুঃখে তিনি তাদের পাশে এসে দাঁড়াতেন।
তিনি ছিলেন তাদের জন্যে একজন দরদী অভিভাবক ও পরামর্শদাতা।
হিন্দু জমিদার ও ইংরেজ ব্যবসায়ীদের অত্যাচার-নিপীড়নের বিরুদ্ধে মুসলিম জনগণকে হাজী শরীয়তুল্লাহ ঐক্যবদ্ধ করে তোলেন।
তিনি হিন্দু জমিদারদের অনেক অবৈধ কর আদায়ের বিরোধিতা করেন।
অবৈধ কর না দেবার জন্যে হাজী শরীয়তুল্লাহ মুসলিম জনগণকে নির্দেশ দিয়েছিলেন কঠিনভাবে।
হাজী শরীয়তুল্লাহ একদিকে রাজনৈতিকভাবে ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হন। আর অপরদিকে সামাজিকভাবে তিনি অত্যাচারী হিন্দু জমিদার ও নীল কুঠিয়ালতের বিরোধিতায় অবতীর্ণ হন।
সেই সাথে বেগবান রাখেন তিনি মুসলমানদের মধ্যে শিরক, বিদআত ও কুসংস্কার দূর করার জন্য সংস্কারের এক মহা বিপ্লবের ধারা।
শরীয়তুল্লাহর এই সংগ্রাম অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। ছড়িয়ে পড়ে গ্রাম থেকে গ্রামাঞ্চলে। বাংলার প্রতিটি ঘরে ঘরে।
ফড়িয়ে পড়ে ফরিদপুর, বরিশা, খুলনা, যশোর, কুষ্টিয়া, ঢাকা, ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা প্রভৃতি জিলায়ও।
তাঁর এই সংগ্রামে যুক্ত হয়েছিলো সমাজের প্রধানত দরিদ্র কৃষক শ্রেণী। যারা হিন্দু জমিদার ও ইংরেজদের অত্যাচার আর শোষণের শিকার ছিলো। হাজী শরীয়তুল্লাহ তাদের ঐক্যবদ্ধ করেন। ঐক্যবদ্ধ করলেন তিনি অসহায়, নিঃস্ব ভাগ্যহত মানুষকে।
তাদেরকে শুনালেন তিনি আশার বাণী।
আঠারো শো সাইত্রিশ সালে তাঁর এই সংগ্রামী আন্দোলনের সদস্য সংখ্যা ছিলো প্রায় বারো হাজারের মতো।
কম কথা!
এই বিপুল সংখ্যক সদস্যের বাইরেও ছিলো একটি বিশাল জনশক্তি।
যারা তাঁর আন্দোলনকে সকল সময় সমর্থন ও সহযোগিতা করতো।
হাজী শরীয়তুল্লাহ ছিলেন প্রকৃত অর্থেই দুঃখী মানুষের জন্যে একজন দায়িত্বশীল অভিভাবক।
গরীবের কষ্ট তিনি সইতে পারতেন না কখনো।
তাই তিনি সকল সময়ই তাদের পাশেগিয়ে দাঁড়াতেন।
এমন জন-দরদী নেতার অভাব ছিল তখন।
হাজী শরীয়তুল্লাহ সময়ের সেই দাবি ও চাহিদা পূরণে তাঁর সর্বশক্তি নিয়োগ করেন।
কৌশলী কর্মপন্থা
খুবই সতর্কতার সাথে হাজী শরীয়তুল্লাহ তাঁর আন্দোলন ও সংস্কারের কর্মপন্থা নির্ধারণ করেছিলেন।
স্থানীয় জমিদার এবং ইংরেজদের সাথে যাতে কোন ধরনের সংঘর্ষ না বাধে, সে ব্যাপারে তিনি সতর্ক ছিলেন।
তিনি নীরবে তাঁর কাজ চালয়ে যাচ্ছিলেন। ফলে দিন দিন তাঁর অনুসারী সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছিল।
কৃষক, তাঁতিসহ সাদারণ মানুষকে হাজী শরীয়তুল্লাহর অধীনে সংঘবদ্ধ হতে দেখে জমিদাররা আতঙ্কিত হতে থাকে।
আগে হিন্দু জমিদাররা তাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে মুসলমান প্রজাদের নিকট থেকে টাকা পয়সা আদায় করতো।
অথচ এটা ছিল ঈমানের সাথে সাংঘর্ষিক।
হাজী শরীয়তুল্লাহ হিন্দুদের পূজার চাঁদা দিতে নিষেধ করেন।
হিন্দু জমিদারদের প্রমাগ গোণার এটাও একটা কারণ ছিল।
এছাড়া এতোদিন মুসলমানরা বিচ্ছিন্ন থাকায় তারা যে কোন ধরনের অত্যাচার করতে পারতো। এবার সেই পথও তাদের বন্ধ হবার উপক্রম হলো। তবু তারা নানাভাবে মুসলমানদের হয়রানি করতে থাকে।
তাই জীবনের শেষ দিকে শক্তি প্রয়োগের কথা ভাবতে থাকেন হাজী শরীয়তুল্লাহ। তারই ফলে দুদু মিয়ার সময় জমিদারদের সাথে সংঘর্ষ হয়েছিল। তবে দুদু মিয়াও বেশ কৌশলে সবদিক মুকাবিলা করেছিলেন। দুদু মিয়া জমিদার এবং নীরকরদের বিরুদ্ধে দুর্বার গতিতে লড়াই করেছেন। তাঁর নেতৃত্বে বাঙালি মুসলমানরা জমিদারদের বিরুদ্ধে সফলতা লাভ করে। এর আগে সাইয়েদ নিসার আলী তিতুমীর জমিদার ও ইংরেজদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ [১৮২৭-১৮৩১] করেছিলেন। কিন্তু তা ব্যর্থতায় রূপ নেয়।
তবে দুদু মিয়া অনেক বেশি সফলতা পেয়েছিলেন।
সরকারের সাথে প্রকাশ্যে বিরোধিতায় না জড়িয়ে প্রথমশত্রু অর্থাৎ জমিদারদের তিনি ঠিকই শায়েস্তা করেছিলে। প্রশাসনিক এবং আইনী সুযোগও তিনি পুরোপুরিভাবে কাজে লাগাবার চেষ্টা করেছেন।
সেই সময়ে আন্দোলনগুলো বা ব্যক্তি মতাদর্শ প্রচারের জন্যে প্রায়ই বহাস নামে বিতর্ক সভার আয়োজন করা হতো।
আর এগুলোর প্রায়ই সমাপ্ত হতো মারামারির মাধ্যমে।
সমস্যার মীমাংসা হওয়ার চাইতে সমস্যা আরো গুরুতর রূপ ধারণ করতো। তাই হাজী শরীয়তুল্লাহ সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়েছিলেন এ ধরনের বিরোধ এড়াতে। তিতুমীর এবং তারিখে মোহাম্মদীর পাটনা গ্রুপের সাথে হাজী শরীয়তুল্লাহর সম্পর্ক ভাল ছিল।
তিনি তাদের আন্দোলনে যোগ না দিলেও পারস্পরিক বিরোধ থেকে তাঁরা সবাই মুক্ত ছিলেন।
মাওলানা কেরামত আলীর আন্দোলনও একই সময়ে পরিচালত হয়েছিল। আহলে হাদীস আন্দোলনও সেই সময় একটু জোরে শোরে শুরু হয়েছিল। মাওলানা কেরামত আলী জৌনপুরি বাঙলায় আসেন ১৮৩৫ সালে।
১৮৭৩৪ সালে ইন্তেকালের পূর্ব পর্যন্ত তিনি বাংলায় ইসলাম প্রচারে নিমগ্ন ছিলেন।
ফরায়েজী আন্দোলনের সাথে তাঁর মূল বিরোধ ছিল ঈদ এবংজুআর নামাজ আদায় না করা এবং খুঁটিনাটি আরো কিছু বিষয়ে।
মাওলানা কেরামত আলী সমাজে প্রচলিত অনেক ব্যাপারে নমনীয় হয়ে কিছুটা ছাড় দেয়ার পক্ষপাতী ছিলেন।
তারিখে মোহাম্মদ আন্দোলন ধর্মীয় আন্দোলন হিসেবে শুরু হয়েছিল ১৮১৮ সালে।
কয়েক বছরের মধ্যেই তা রাজণৈতিক আন্দোলন রূপ নেয়।
কিন্তু নিম্ন বাংলার কৃষক সমাজের কাছে সেটা তেমন সাড়া জাগাতে পারেনি। সাইয়েদ আহমদ শহীদের আন্দোলন দিনাজপুর, মালদহ, রাজশাহী, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, বর্ধমান, যশোর, কলকাতা এবং চব্বিশ পরগনায় জোরালো ছিল। অর্থাৎ গঙ্গা এবং ভাগিরথি নদীর দু’কূলে ছিল তাদের প্রচার ভূমি।
একই সময়ে এতগুলো সংস্কার আন্দোলন ও শোষণ-নিপীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রাম অব্যাহত ছিল।
কিন্তু কোনো নেতা অন্যের আন্দোলনকে অবজ্ঞা করেননি।
লিপ্ত হননি সরাসরি কোনো বিরোধিতায়।
হাজী শরীয়তুল্লাহ এই সময় অত্যন্ত কৌশলী কর্মপন্থা গ্রহণ করেন।
দারুল হরব
হাজী শরীয়তুল্লাহ যখন মক্কায় চিলেন, তখন তাঁর পরিচয় ঘটে মক্কার মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাব নজদর ইসলামী সংস্কার আন্দোলনের সাথে। এই আন্দোলনের প্রতি হাজী শরীয়তুল্লাহ আকৃষ্ট হযে পড়েন।
দিল্লিতে শাহ আবদুল আযীয দেহলভীর নেতৃত্বে ভারতেও আবদুল ওয়াহ্হাব নজদীর অনুকরণে ইসলামী সংস্কার আন্দোলন শুরু হয়।
তিনি ভরবর্ষকে ‘দারুল হরব’ বলে ঘোষণা করেন।
‘দারুল হরব’ কে ‘দারুল ইসলাম’ তথা একটি ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্যে যাঁরা অক্লান্তভাবে চেষ্ট করেছিলেন।
তাঁদের মধ্যে ছিলেন সাইয়েদ আহমদ বেরেলভী,শাহ আবদুল আযীযের ভ্রাতুষ্পুত্র শাহ ইসমাইল ও জামাতা মাওলানা আবদুল হাই।
হাজী শরীয়তুল্লাহও এদেশকে ‘দারুল হরব’ ঘোষণা করেন।
তিনি ঘোষণা দেন, এদেশ যতোদিন ‘দারুল ইসলাম’ না হবে, ততোদিন এখানে ‘জুমআ’ ও ঈদের নামায হবে না।
হাজী শরীয়তুল্লাহ এদেশে যেমন ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্যে চেষ্টা করেছেন, ঠিক তেমনি অন্য দেশেও ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্যে তাঁর অবদান ছিলো অসামান্য।
তিনি সাইয়েদ আহমদ বেরেলভীর ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের কাজে সহায়তা করার জন্যে এদেশ থেকে বহু মুজাহিদ এবং যাকাত, ফিতরা থেকে সংগৃহীত অর্থসহ নানা ধরনের সাহায্য ভাতের সিত্তানা কেন্দ্রে পাঠাতেন।
জুলুম নির্যাতন
যে কোনো ভালো কাজ করতে গেলেই দুষ্ট লোকেরা বাধ সাধে। বাধ সাধে এজন্যে যে, তাদের স্বার্থে আঘা লাগে।
হাজী শরীয়তুল্লাহও বিনা বাধায় কাজ করতে পারেননি।
তাঁর আন্দোলনী জীবনে বারবার বাধা এসেছে। বাধা এসেছে জমিার ও ইংরেজদের পক্ষ থেকে।
তাঁর কর্মীদের পুলিশ নির্মমভাবে অত্যাচার করেছিলো।
তাঁকেও সইতে হয়েছিলো নানা ধরনের নিপীড়ন। তাঁকে রামনগর থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিলো।
আঠারো ঊনচল্লিশ সাল পর্যন্ত তাঁকে বেশ কয়েকবার গ্রেফতারও করা হয়েছিলো।
কিন্তু কোনোভাবেই হিন্দু জমিদার এবং ইংরেজরা পরাস্ত করতে পারেননি সত্যের সৈনিক হাজী শরীয়তুল্লাহকে।
বরং তাদের পক্ষ থেকে যতোই বাধা আসতো ততোই তিনি তাঁর সংগ্রামী ভূমিকা পালন করে যেতেন দুর্বার গতিতে।
সামনে এগিয়ে যেতেন দিগুণ সাহসের সাথে।
হাজী শরীয়তুল্লাহর নতুন কর্মক্ষেত্র ছিলো ঢাকা জিলার নয়া বাড়িতে।
কিন্তু হিন্দু জমিদারদের চরম বিরোধিতার ফলে তিনি ঢাকার নয়া বাড়ি ছাড়তে বাধ্য হন।
এখান থেকে ফিরে যান তিনি তাঁর নিজের গ্রাম- শামাইলে।
সেখানে থেকেই হাজী শরীয়তুল্লাহ পূর্ণ গতিতে ফরায়েজী আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতে থাকেন।
অত্যাচারী হিন্দু জমিদার, নীল কুঠিয়াল এবং ইংরেজ দস্যুরা আরো বেশি ক্ষেপে গেলো হাজী শরীয়তুল্লাহর ওপর।
জুলুম-অত্যাচার ছাড়াও হাজী শরীয়তুল্লাহ এবং তাঁর আন্দোলন সম্পর্কে সে সময়ে বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হলো না প্রকার কল্পকথা।
যেসব কথার কোনো ভিত্তিই ছিলো না।
তাতে ছিলো না সত্যের লেশ মাত্র।
এখানে মাত্র একটি উদাহরণ দিলেই ব্যাপারটি বুঝা যাবে সহজে।
পত্র-পত্রিকার ভাষ্য
হিন্দু যে ফরায়েজী আন্দোলনকে মোটেই সহ্য করতে পারতো না তা বুঝা যায় তাদের পত্রিকা ‘সমাচার দর্পণের’ ভাষ্য থেকেই।
আঠারো শো সাইত্রিশ সালের বাইশে এপ্রিল তারিখে এই পত্রিকায় একটি পত্র ছাপা হয়। পত্রটি ছিলো এ রকম:
“ইদানিং জিলা ফরিদপুরের আন্তঃপিাতি শিবচর থানার সরহদ্দে বাহাদুরপুর গ্রামে সরিতুল্লাহ নামক একজন বাদশাহী লওনেচ্ছুক হইয়া ন্যূনাধিক বার হাজার জোলা ও মুসলমান দলবদ্ধ করিয়া নতুন এক সরা জারি করিয়া নজ মতাবলম্বী লোকদিকের মুখে দাড়ি, কাছা খোলা, কটি দেশের ধর্মের রুজ্জুভৈল করিয়া তৎতুর্গিস্থ হিন্দুদিগের বাড়ি চড়াও হইয়া দেবদেবী পূজার প্রতি অশেষ প্রকার আঘাত জন্মাইতেছে- এই জিলা ঢাকার অন্তঃপাতি মতলবগঞ্জ থানার রাজনগর নিবাসী দেওয়ান মৃত্যুঞ্জয় রায়ের স্থাপিত দ্বাদশ শিবলিঙ্গ ভাঙ্গিয়া নদীতে বিসর্জন দিয়াছে এবং ঐ থানায় সরহদ্দে দ্বাদশ শিবলিঙ্গ ভাঙ্গিয়া নদীতে বিসর্জন দিয়াছে এবং ঐ থানার সরহদ্দে পোড়াগাছা গ্রামে একজন ভদ্রলোকের বাটিতে রাত্রিযোগে চড়াও হই সর্বস্ব হরণ করিয়া তাহার গৃহে অগ্নি দিয়া অবশিষ্ট যেটুকু ছিল ভষ্ম রাশি করিলে একজন যবন মৃত হইয়া ঢাকায় দাওরায় অর্পিত হইয়াছে।
... আর শ্রত হওয়া গেল, সরিতুল্লাহ দলভুক্ত দুষ্ট যবনের ঐ ফরিদপুরের অন্তঃপাতি পাটকান্দা গ্রামের বাবু তারিনী চরণ মজুমদারের প্রতি নানা প্রকার দৌরাত্ম্য অর্থাৎ তাহার বাটিতে দেবদেবী পূজায় আঘাত জন্মাইয়া গোহত্যা ইত্যাদি কুকর্ম উপস্থিত করেলে মজুমদার বাবু যবনদিগের সহিত সম্মুখ যুদ্ধ অনুচিত বোধ করিয়া- ঐ সকল দৌরাত্ম্য ফরিদপুরের ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের হুজরে জ্ঞাপন করিলে ঐ সাহেব বিচারপূর্বক কয়েকজন যবনকে কারাগারে বদ্ধ করিয়াছেন এবং এ বিষয়ে বিলক্ষণ অনুসন্ধান করিতেচেন। সে সম্পাদক মহাশয়, দুষ্ট যবনেরা মফঃস্বলে এ সকল অত্যাচার ও দৌরাত্ম্যে ক্ষান্ত না হইয়া বরং বিচার গৃহে আক্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। শ্রুত হওয়া গেল, ফরিদপুরের ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের হুজরে যে সকল আমলা ও মোক্তার-কারেরা নিযুক্ত আছে, তাহারা সকলেই সরিতুল্লাহ যবনের মতাবলম্বী- তাহাদের রীতি এই যদি কাহার নামে মিথ্যা অভিযোগ করিতে হয়, তবে কেহ ফরিয়াদী কেহ বা সাক্ষী হইয়া মোকদ্দমা উপস্থিত করে সুতরাং ১২০০০ লোক দলবদ্ধ। ইহাতে ফরিয়াদীর সাক্ষীর ত্রুটি কি আছে... আমি বোধ করি, সরিতুল্লাহ যবন যে প্রকার দলবদ্ধ হইয়া উত্তর উত্তর প্রবল হইতেছে অল্পদিনের মধ্যে হিন্দু ধর্ম লোপ পাইয়া অকালে প্রলয় হইবেক। সরিতুল্লাহর চোটপাটের শত অংশের এক অংশ তিতুমীর করিয়াছিল না। ইতি সন ১২৪৩ সাল, তারিখ ২৪শে চৈত্র।”
সুতরাং এই একটি মাত্র চিঠির মাধ্যমেই পরিষ্কার হয়ে যায় যে, হাজী শরীয়তুল্লাহকে কত ভাবে আক্রমণ করা হয়েছিল!
তাতে কি!
সাহসী সৈনিক কি থেমে যায় কখনো? না!
হাজী শরীয়তুল্লাহও থেমে থাকেননি।
বরং তিনি অত্যন্ত সাহসিকতা ও দৃঢ়তার সাথে সকল বাধা ও প্রতিবন্ধকতা মুকাবিলা করে ক্রমাগত এগিযে গেছেন সামনের দিকে। ক্রমাগত সামনের দিকেই।
সমাজ সংস্কারক
দীর্ঘদিন হিন্দুদের সাথে মিলে মিশে এবং তাদের পাশাপাশি থাকার কারণে এবং যথাযথ ধর্মীয় বোধ না থাকার কারণে মুসলমানদের মধ্যে হিন্দু সমাজের অনেক রীতি নীতি ও ধ্যান ধারণা প্রবেশ করেছিলো।
যা ছিলো ইসলামের আকীদা বিশ্বাসের সম্পূর্ণ বিপরীত।
ছিল শিরক বিদআত পর্যায়ের।
হাজী শরীয়তুল্লাহ শরক বিদয়াত, পীর-ফকিরের মাজারে সিজদা, মানব ও হিন্দুদের পূজার মতো নানা খারাবী ও বাড়াবাড়ি ইসলামের মৌলনীতি কুরআন ও হাদীসের বিপরীত বলে ঘোষণা করেন।
তিনি সকল মুসলমানকে এসব কাজ থেকে বিরত থাকার জন্যে জোর আহ্বান জানান।
হাজী শরীয়তুল্লাহই এদেশে প্রথম শরীয়ত, তরীকতের ধারক ও বাহক পীরদের মর্যাদা সম্পর্কে মানুষকে জানান।
তাঁদের সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে বলেন যে, তাঁরা শিক্ষকের মতো। এর বেশি কিছু নয়।
অতেএব তাঁদেরকে শ্রদ্ধা করা যায়, কিন্তু এর বেশি আর কিছু করা যাবে না। অথচ তখনকার মুসলমানদের ধারণা ছিল যে, পীরেরা তাদের মুরীদানকে আল্লাহর কাছে সুপারিশ করে জান্নাতে নিয়ে যেতে পারবেন।
তাই অনেক মুরীদ খারাপ কাজে লিপ্ত থাকতো।
তারা ঠিকভাবে আল্লাহর হুকুম মেনে চলতো না।
তাদের বিশ্বাস ছিলো আমল এবং আখলাকে ঘাটতি থাকলেও পীর সাহেব তাদেরকে পার করে দিতে পারবেন।
জান্নাতে যাবার জন্যে যা যা দরকার তিনি সব বন্দোবস্ত করে দেবেন। কি সর্বনেশে চিন্তা!
হাজী শরীয়তুল্লাহ তাদের এইসব ভুল ধারণা ভেঙ্গে দেন।
হাজী শরীয়তুল্লাহ বিবাহ এবং অন্যান্য সামাজিক উৎসবগুলোতে অযথা খরচ করার বিরোধিতা করেন।
মুসলমান জাতির আর্থিক উন্নয়নের জন্যে তিনি বিশেষভাবে সচেষ্ট ছিলেন। আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ভয় না করার জন্যে তিনি সকেলর প্রতি আহ্বান জানান।
কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী সকল কাজ সম্পাদন করার জন্যে তিনি সকলকে নির্দেশ দেন।
হাজী শরীয়তুল্লাহকে এক সাথে অনেকগুলো শক্তিকে মুকাবিলা করতেহয়েছে। জাঁকিয়া বসা পীর তন্ত্র, নানা মারমী তরীকা, শিয়া মাজহাব, মাওলানা কেরামত আলীর আন্দোলন এবং সর্বোপরি স্থানীয় জমিদার এবং ইংরেজ শাসকবৃন্দকে তাঁকে শক্তভাবে মুকাবিলা করতে হয়েছে।
পীর ব্যবস্থাটি বাংলার মুসলমান সমাজে এতো গভীরভাবে প্রবেশ করেছিল যে, আত্ম-মর্যাদাবান জাতি হিসেবে অস্তিত্ব ঘোষণার জন্য সেই সময়ে এই প্রভাব থেকে বেরিয়ে আসা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ।
এদশে ইসলাম প্রচার ও প্রসারে পীর দরেবেশদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। বলতে গেলে তখনকার দিনে ধর্মীয় বিধি বিধান সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জনের প্রধান মাধ্যমই ছিল তাঁরা।
কিন্তু ঊনবিংশ শতকের ঘোর অমানিশার সময়ে পীর-দরবেশ নামে অনেকেই বিভ্রান্ত ছড়াতো।
তাছাড়া মৃত অনেক পীরের নামে মানত করা, তাদের মাজারে শিরনি দেওয়ার রেওয়াজ ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল্
পাঁচ পীর, মানিক পীর, ঘোড়া পীর, মাদারী পীর, খাজে খিজির, জিন্দা গাজী, বদর পীর প্রমুখের প্রতি শিরনি বা মানত না করে কেউ কোনো কাজে হাত দিত না।
পীর ভক্তি তখন শিরকের পর্যায়ে চলে গিয়াছিল।
মুসলমানদের এই বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত করা ছিল খুবই প্রয়োজনীয় একটি কাজ। তাই হাজী শরীয়তুল্লাহ এক্ষেত্রে ইসলামী চেতনার বিস্তার ঘটান।
পীর, সুফি, শেখ প্রভৃতি মাধ্যম বাদ দিয়ে আল্লাহর সাথে বান্দার সরাসরি সম্পর্কের কথা প্রচার করলেন।
শিক্ষার জন্যে কোনো মাধ্যম অবশ্যই প্রয়োজন।
তাই তিনি উস্তাদ-শাগরেদ ব্যবস্থা কায়েম করে নতুন দিগন্তের সূচনা করলেন। অবশ্য পরবর্তীকালে অনেকটা পীরদের মতোই তাঁর বংশধররাই ফরায়েজী আন্দোলনের প্রধান নির্বাচিত হতেন।
তবে এক্ষেত্রে আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের মতামত প্রয়োজন হতো।
হাজী শরীয়তুল্লাহ জানিয়ে দিলেন, সত্যিকারের মুসলমান হওয়ার জন্য কোনো পীর দরবেশের প্রয়োজন নেই।
জাঁকজমকপূর্ণ কোনো অনুষ্ঠানেরও দরকার নেই।
আল্লাহ ও তাঁর নবীকে (সা) স্বীকার তথা তৌহিদ ও রিসালাতে বিশ্বাস এবং ফরজ পালনের মধ্যেই যাবতীয় মুক্তি নিহিত রয়েছে।
এভাবে হাজী শরীয়তুল্লাহ মানুষকে সঠিক পথের সন্ধান দেন।
অন্যায় জুলুমরে বিপরীতে তিনি সকল মানুষকে এক হবার জন্যে তাকিদ দেন।
তাঁর এ মুক্তির আহ্বানে সাড়া দিয়ে মুসলমানরা সেদিন সংগ্রাম ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো।
হাজী শরীয়তুল্লাহর সংস্কার তথা ফরায়েজী আন্দোলন মূলত রাজ্যহারা, সম্পদহারা মুসলিম জাতির মনের আশা ও ভরসা এনে দিয়েছিলো।
তাঁর এ আন্দোলনের জন্যে যেন হাজার হাজার মুসলমান বহুদিন থেকে অপেক্ষায় প্রহর গুণছিলো।
সেই সুযোগ যখন এলো, তখন তাঁর কথায় এক সাথে সকলেই জেগে উঠলো অসহায় মুসলমানের মুক্তির জন্যে।
কম বিস্ময়ের ব্যাপার নয়!
অত্যাচারী জমিদারদের বিরুদ্ধে তারাও সোচ্চার হয়ে ওঠে হাজী শরীয়তুল্লাহর নেতৃত্বে।
ঝাঁপিয়ে পড়ে তারা সকল প্রকার ত্যাগ স্বীকার করে।
হাজী শরীয়তুল্লাহর এই সংস্কার প্রচেষ্টা বিফলে যায়নি। যাবার কথাও নয়।
সত্যিই একদিন তাঁর ফরায়েজী আন্দোলন সফলতার দ্বাপ্রান্তে উপস্থিত হয়েছিলো।
এ সম্পর্কে জেম্স ওয়াইজ তাঁর মোহামেডানস অব ইস্টার্ণ বেঙ্গল’ গ্রন্থে বলেন:
“হিন্দুদের বহু ইশ্বরবাদ নীতির সাথে দীর্ঘদিনের সম্পর্কের ফলে মুসলমানদের মধ্যে যেসব কুসংস্কার ও দুর্নীতি দেখা দিয়েছিল তার বিরুদ্ধে কথা বলার প্রথম সোচ্চার প্রচারক হিসেবে তাঁর [হাজী শরীয়তুল্লাহ] আবির্ভাব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। কিন্তু বাংলার চেতনাহীন ও উদাসীন চাষী সমাজের মধ্যে তিনি উৎসাহ-উদ্দীপনা জাগ্রত করার ব্যাপারে যে সাফল্য অর্জন করেন, তা আরও বেশী চমকপ্রদ।
এ উদ্দেশ্যে সাধনের জন্যে একজন অকপট ও সহানুভূতিসম্পন্ন প্রচারকেরই প্রয়োজন ছিল। আর মানুষের মনে প্রভাব বিস্তারের অধিকতর ক্ষমতা শরীয়তুল্লাহর চেয়ে অপর কারুর মধ্যে কখনও দেখা যায়নি।”
হাজী শরীয়তুল্লাহ ছিলো উন্নত চরিত্র। ছিলো তাঁর অতুলনীয় মানবীয় গুণ ওবৈশিষ্ট্য।
সেই চমৎকার আকর্ষণীয় এবং মোহনীয় শক্তি ছিলো তাঁর। আর এজন্যই তাঁর চরিত্রে মুগ্ধ ছিলো হাজার হাজার মুসলমান।
আদর্শ ও চরিত্রের গুণেই তিনি জয় করেছিলেন ভাগ্যহত মানুষের মন।
তাঁর নির্মল চরিত্রের প্রশংসা করতে গিয়ে ডক্তর ওয়াইজও বলতে বাধ্য হয়েছেন যে,
“তাঁর নির্দেশ ও আদর্শ চরিত্র দেশবাসীদের ভক্তিশ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। দুর্যোগের দিনে সৎ পরামর্শ ও ব্যথা-বেদনায় সান্ত্বনা প্রদানকারী পিতার মতোই দেশের জনগণ তাঁকে ভালোবাসতেন।”
প্রকৃত অর্থেই হাজী শরীয়তুল্লাহ ছিলেন একজন নির্ভীক ও নিবেদিত-প্রাণ সমাজ সংস্কারক।
এদেশের মুসলমানদের চরম দুর্দিনে তিনি যোগ্য অভিভাবকের মতো তাদের কাছে টেনে নিয়েছিলেন।
দেখিয়েছিলেন সত্য-সঠিক পথ।
এজন্যই ইতিহাসের পাতায় এখনো জ্বল জ্বল করে আছে তাঁর নাম- হাজী শরীয়তুল্লাহ!
হান্টারের পরিচয়
হান্টারের পুরো নাম ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার।চাকরি কতেন বৃটিশের অধীনে।
তিনি ছিলেন বৃটিশের একজন পদস্থ রাজকর্মচারী।অন্যান্য ইংরেজদের মতো হান্টারও ছিলেন মুসলমানদের বিদ্রোহের ঘোর বিরোধী। মুসলিম বিদ্ধেষী তো বটেই। হান্টারের যোগ্যতা ছিলো লেখায়।
তিনি ভালো লিখতে পারতেন। তার এই যোগ্যতার কারণে ইংরেজ তাকে দায়িত্ব দিয়েছিলো মুসলমানদের বিদ্রোহ সম্পর্কে গোপন তথ্য সংগ্রহের। তার বিশেষ দায়িত্ব ছিলো সৈয়দ আহম শহীদের আন্দোলনের ওপর রিপোর্ট তৈরি করে বৃটিশ সরকারের কাছে পেশ করা।
ইংরেজের দেয়া এই দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে হান্টার তৎকালীন মুসলমানদের আন্দোলন ও বিদ্রোহ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। ‘দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস্’ নামে একটি গ্রন্থও তিনি লেখেন।
এই গ্রন্থে হান্টার বিভিন্ন জায়গায় মুসলমানদের আন্দোলন ও বিদ্রোহ সম্পর্কে তীর্যক-তীক্ষ্ম ভাষায় অনেক কিছুর উল্লেখ করেছেন।
হান্টার মুসলমানদের কোনো বন্ধু ছিলেন না।
তিনি তার দায়িত্ব পালনের জন্যে মুসলমান ও তাদের আন্দোলন সম্পর্কে যা আলোচনা করেছেন তা মুসলমানদের কল্যাণের জন্য করেননি।
করেছেন ইংরেজদের হুকুম পালন করার জন্যে।
তাদের তুষ্টির জন্যে।
তবুও তার এই পর্যালোচনা রিপোর্ট এবং তার মতামতের মধ্যে মুসলমানদের শৌর্য, সাহস ও আন্দোলন তৎপরতা সম্পর্কে হান্টার যে তথ্য পরিবেশন করেছেন তা আমাদের জন্যে আজো রীতিমত বিস্ময়ের ব্যাপার! তার অনেক সত্য উচ্চারণের মাধ্যমে আমরা সেই সময়কার একটি চালচিত্র পেয়ে যাই।
এখানে হান্টারের কয়েকটি অভিমত উপস্থাপানের মধ্য দিয়ে তখনকার আন্দোলন-বিদ্রোহ সম্পর্কে আমরা কিছুটা ধারণা লাভ করবো।
হান্টারেরর অভিমত
‘দি ইন্ডিয়অন মুসলমানস্’ গ্রন্থে মিঃ হান্টার ইংরেজদের তাবেদার হয়েও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে,
“গাঙ্গের ব-দ্বীপ এলাকার ধর্মান্ধ মুসলমানরা নিজেদের ওয়াহাবী না বলে ফরায়েজী অর্থাৎ ইসলাম ধর্মের অনাবশ্যকীয় আচারানুষ্ঠানাদি বর্জন হিসেবে পরিচিত করে।... কলকাতার পূর্ব দিকের জেলাসমূহে এদের সংখ্যা বিপুলভাবে বৃদ্ধি পায়। ১৮৪৩ সালে এই সম্প্রদায়টি এতদূর বিপজ্জনক হয়ে ওঠে যে, তাদের সম্পর্কে তদন্তের জন্যে সরকারকে বিশেষ তথ্যানুসন্ধান কমিশন নিয়োগ করতে হয়। বাংলার পুলিশ প্রধান কর্তৃক প্রদত্ব রিপোর্টে বলা হয় যে, মাত্র একজন প্রচারক [হাজী শরীয়তুল্লাহ] প্রায় আশি হাজার অনুগামীর এক বিরাট দল গড়ে তুলেছে এবং তারা প্রত্যেকের ব্যক্তিগত স্বার্থেকে গোটা সম্প্রদায়ের স্বার্থ বলে বিবেচনা করে থাকে।”..
‘দি ইন্ডিয়ান মুসলানস্’ গ্রন্থে হান্টার আরো বলেন:
“সারা ভারতে তাদের প্রতিনিধি পাঠিয়ে ইতিহাসের এক বৃহত্তম ধর্মীয় পুনরুত্থান সাধিত করল তারা। তাঁদের অসংখ্য ছোট ছোট মিশনারী দল ছিল। দক্ষ সংগঠনের মাধ্যমে তারা মুরীদগণের তাকিদে যেখানে প্রয়োজন সেখানেই আস্তানা স্থাপন করতে পারত।... প্রত্যেক জেলাতেই একজন করে প্রচারক নিযুক্ত হয়। ভ্রাম্যমান মিশনারীরা মাঝে মাঝে এই সকল জেলা সফর কালে সেখানকার স্থায়ী প্রচারকদের উদ্যমকে জাগ্রত রাখতে থাকে। এইসব প্রচারকদের অশুভ প্রভাব ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল।.. এরা এমন ধর্মান্ধদের তহবিলে দান করেছিল... দলের পর দল সংগ্রহ করে ধর্মান্ধ শিবিরে পাঠিয়ে দেয়া হচ্ছিল। দেশের সর্বত্র মুসলমান জনসাধারণের মধ্যেতারা গভীর আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল... অজস্র রাজদ্রোহমূলক সাহিত্য, পাটনায় অবস্থিত কেন্দ্রীয় প্রচার কেন্দ্র এবং সারা বাংলার আনাচে কানাচে প্রচারকদের আনাগোনা ছাড়াও জনগণের মধ্যে রাজদ্রোহমূলক কাজে উৎসাহ সৃষ্টির জন্যে ওয়াহাবীরা [?] একটু চতুরথ সংগঠন গড়ে তুলেছে।... এইভঅবে পল্লী বাংলার বিভিন্ন স্থানে এক ধরনের বিদ্রোহী কলোনী গড়ে উঠেছে।... অর্থ সংগ্রহ ব্যবস্থাটা সহজ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল। গ্রামগুলোকে বিভিন্ন আর্থিক এলাকায় বিভক্ত করে প্রত্যেক এলাকার জন্যে একজন করে প্রধান ট্যাক্স আদায়কারী নিয়োগ করা হয়। যে গ্রামের জনসংখ্যা খুব বেশী সেখানে একাধিক আদায়কারী নিয়োগ করা হয় এবং তার মধ্যে একজন মৌলবী থাকতেন যিনি সমাজে ইমামতি করতেন.... একজন জেনারেল ম্যানেজার রাখা হয় যিনি মুসলমানদের দুনিয়াবী কাজের তদারক করতেন। এছাড়াও একজন অফিসার থাকতেন, তার কাজ ছিল বিপদজনক চিঠি-পত্র বিলি বন্টন ও রাজদ্রোহমূলক খবরাখবর আদান প্রদান করা।..”
হান্টর তার লেখায় ‘ওহাবী’ বলে যে সংগঠনের কথা বলেছেন আসলে তা আদৌ সঠিক নয়।
এটা ছিলো সম্পূর্ণ মিথ্যাচার।
‘ওহাবী’ বলতে পৃথিবীতে কোনো সংগঠনের অস্তিত্ব ছিল না।’
‘ওয়াহাবী’ বা ‘ওহাবী’ পরিভাষাটি ইউরোপীয়দের কল্পনারাজ্যের সৃষ্টি এবং ইসলামী আন্দোলনের জন্যে একটি গালি মাত্র।
সাইয়েদ আহমদ বেরেলভীর ‘জিহাদী আন্দোলনকে’ উপহাস করার জন্যে তারা তাদেরকে ‘ওহাবী’ বলে আখ্যায়িত করেছেন।
এটা ছিলো তাদের ঘৃণ্য এক পরিভাষা।
যেটা এখনো কাম্য ছিলো না।
প্রকৃত অর্থে ‘ওহাবী’ কথাটি সম্পূর্ণ সত্যের খেলাফ এবং ইসলাম বিরোধী। তাদের শত ষড়যন্ত্র আর অপপ্রচরের মধ্যেও ইংরেজের রিুদ্ধে এ সময় বিরামহীন সংগ্রাম চলছিলো।
ইংরেজরা তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করে চেয়েছিলো মুসলমানদের সংগ্রামকে প্রতিহত করতে।
কিন্তু তারা তা পারেনি।
পারেনি শত চেষ্টা করেও এই সংগ্রামকে দমাতে।
এ প্রসঙ্গে হান্টারের একটি উদ্ধৃতি এখানে উল্লেখযোগ্য। তিনি লেখেন:
“আমাদের সীমান্ত অঞ্চলে ১৮৩১ খৃস্টাব্দ থেকে শুরু করে ১৮৬৮ খৃস্টাব্দ তাদের বিরুদ্ধে আমাদের সর্বশেষ অভিযান পর্যন্ত ইতিহাস আলোচনা করলাম। ওহাবীরেদ [?] যুদ্ধাত্মক তৎপরতা ভারতের সর্বত্র যে বিস্তার লাভ করেছিল তার ইতিহাস আলোচনা করতে গেলে এই গ্রন্থের কলেবর বিরাট আকার ধারণ করবে... ধর্মান্ধদের দ্বারা সীমান্তে বিরামহীন অশান্তি বিরাজমান রাখা ছাড়াও তিনবার বৃহদাকার ঐক্যজোট সংঘটিত হয়েছে এবং প্রত্যেক বারই বৃটিশ ভারতকে একেকটি যুদ্ধের মাধ্যমে তার মুকাবিলা করতে হয়েছে।... কিন্তু এদের নির্মূল করার জন্যে আমাদে সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।... নিজেদের অবস্থা শেষ পর্যন্ত যে ভেঙ্গে পড়েছে তার নিদর্শন তাদের নিজেদের অবস্থা থেকেই বুঝা যাচ্ছে। তাদের প্রধান নেতারা ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার হয়েছে এবং অবশিষ্টরাও বুঝতে পেরেছে যে সক্রিয় হলে তাদেরও একই পরিণামের সম্মুখীন হতে হবে। কিন্তু সীমান্তের সশস্ত্র বিরাট ধর্মীয় মহা সম্মিলন রূপ গ্রহণ করবে। আজ সকালেই [১৪ই জুন, ১৮৭১] আমি এই পরিচ্ছেদ রচনার কাজ শেষ করার সময় জানতে পারলাম যে, ব্লাক মাউন্টেনের উপর বিদ্রোহী শিবির থেকে আরেকটি আক্রমণ পরিচালিত হয়েছে।”
তখনকার আন্দোলন সম্পর্কে হান্টারের আর একটি বিবেচনা:
“বাংলার মুসলমানরা আবার বিচিত্র রূপ ধারণ করেছে, গ্রাম পড়িয়েছে, আমাদের প্রজাদের হত্যা করেছে এবং আমাদের সীমান্তের ওপরে মাসের পর মাস ধরে গড়ে ওঠা শত্রু-বসতির লোক নিয়মিতভাবে সংগ্রহ করা হয়েছে বাংলাদেশের অভন্তরে থেকে। বিভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত রাজনৈতিক মোকাদ্দমার বিচার থেকে একথাই প্রমাণিত হয় যে, আমাদের প্রদেশসমূহের সর্বত্র বিস্তারিত হয়েছে এক ষড়যন্ত্রের জাল। পাঞ্জাবের উত্তরে অবস্থিত জনহীন পর্বতরাজির সঙ্গে উষ্ণ মণ্ডলীয় গঙ্গা অববাহিকার জলাভূমি অঞ্চলের [বাংলার] যোগসূ্ত্র স্থাপিত হয়েছে রাজদ্রোহীদের নিরবিচ্ছিন্ন সমাবেশের মাধ্যমে। সুসংগঠিত প্রচেষ্টায় তারা ব-দ্বীপ অঞ্চল [বাংলা] থেকেঅর্থ ও লোক সংগ্রহ করে এবং দুই হাজার মাইল দূরে অবস্থিত বিদ্রোহী শিবিরে তা চালান করে দেয়।... বাংলার এমন কোন জনপদ ছিল না যেখানকার মুসলমানদের মধ্যে সৈয়দ সাহেবের সংস্কারের বাণী ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেনি। প্রতিটি ধার্মিক পরিবারের যুবকরা সীমান্তে গিয়ে জিহাদ করার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করত। বৃটিশ সরকারের গোয়েন্দার চোখ ফাঁকি দিয়ে একদিন তারা হঠাৎ করে সীমান্তের মুজাহিদ কাফেলায় যোগ দেবার উদ্দেশ্যে বের হয়ে পড়ত। জমির খাজনা পরিশোধ করতে অসমর্থ কৃষকরাও জিহাদের জন্য নিয়মিত অর্থ প্রদান করতে কুণ্ঠিত হতো না।”
হান্টারের লেখায় এই ভাবেই বিষেদগারের পাশাপাশি অনেক সত্যও বেরিয়ে আসে।
কয়েকটি বিবেচনা
ফরায়েজী আন্দোলনকে বিশ্লেষণ করে প্রাজ্ঞজনেরা কয়েকটি বিবেচনায় উপনীত হয়েছেন। বিবেচনায় উপনীত হয়েছেন। বিবেচনাগুলো:
১. মহান মর্দে মুজাহিদ হাজী শরীয়তুল্লাহর গড়ে তোলা এই আন্দোলন ছিলো পূর্ব ভারতের প্রথম একমাত্র ইসলামী আন্দোলন।
যার লক্ষ্য ছিলো বিদেশীদের হাত থেকে মুসলমানদের স্বাধীন ও মুক্ত করা এবং সংগঠিত করা।
২. হাজী শরীয়তুল্লাহর এই আন্দোলন কোনো সাময়িক আবেগতাড়িত ব্যাপার ছিলো না, বরং এটি ছিলো একটি প্রাণবন্ত আন্দোলন।
আর এই কারণেই এতো দীর্ঘ সময় ধরে আমরা এর প্রাণস্পন্দন দেখতে পাই।
৩. প্রথম দিকে এই আন্দোলন ছিলো ইসলামী সংস্কারমূলক। কারণ তখনকার কর্মসূচী ছলো আকীদা বিশ্বাসের সংশোধন এবং বিদয়াতমূলক আচার অনুষ্ঠান উচ্ছেদ।
কিন্তু পরবর্তীকালে ধীরে ধীরে সামাজিক ও রাজনৈতিক দিকগুলো ও এর সাথে যুক্ত হয়ে যায়।
এমনকি এক পর্যায়ে সময়ের প্রয়োজনে লাঠিয়াল বাহিনীরূপে সামরিক শক্তিও গড়ে তোলা হয়।
৪. ফরায়েজী আন্দোলনের আকীদা বিশ্বাসের কথা বলতে গেলে বলতে হয়, এই বিপ্লবের প্রতি ঐতিহাসিকরা যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করেনন। বরং বিকৃতভাবে তারা সেটা উপস্থিাপিত হয়েছে।
কারণ তাদের লেখায় আকীদা বিশ্বাসের তুলনায় এই আন্দোলনের সামাজিক কাজকর্ম বেশি মাত্রায় ফুটে উঠেছে। অথচ আকীদা বিশ্বাসের সংশোধন এবং ধ্যান ধারণা পরিশুদ্ধির ক্ষেত্রেও এই আন্দোলন ব্যাপক তথা প্রধান ভূমিকা পালন করেছে।
৫. এই আন্দোলন ছিলো ইসলামী আদর্শভিত্তিক স্বাধীনতা আন্দোলন।
এতে যেমন ঈমান আকীদার পরিশুদ্ধির প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছিলো তেমনি সাধারণ মানুষের অধিকার আদায়েরও বলিষ্ঠ প্রতিশ্রুতি এতে ছিলো। এর ছায়াতলে সংঘবদ্ধ হতে অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলো অসংখ্য কৃষক। তাই এ আন্দোলনকে কৃষক আন্দোলনও বলা যায়।
প্রতিপক্ষের শ্যৈন দৃষ্টি
হিন্দুরা কখনই মুসলমানদেরকে সুনজরে দেখেনি।
তারা মুসলমানদের ইংরেজ-বিরোধী আন্দোলনকেও সহ্য করতে পারতো না। তারা ইংরেজদেরকে তুষ্ট করার জন্যে সর্বদা তৎপর থাকতো।
আর মুসলমানদের বিরোধিতা করাই ছিলো তাদের মজ্জাগত স্বভাব।
আঠারো শো সাতান্ন সালে যখন স্বাধীনতা সংগ্রামী ইংরেজের কামানের গোলায় জীবন দিচ্ছিলো, তখন হিন্দু পত্রিকায় লেখা হয়েছিলো:
“আমরা পরমেশ্বরের সমীপে সর্বদা প্রার্থনা করি, পুরুষানুক্রমে যেন ইংরেজাধিকার থাকিতে পারি। ভারত ভূমি কত পুণ্য করিয়াছিলেন এই কারণে ইংরেজ স্বামী পাইয়াছেন, মৃত্যুকাল পর্যন্ত যেন ইংরেজ ভূপালদিগের মুখের পান হইয়া পরম সুখে কাল যাপন করেন।” [সংবাদ ভাস্কর: ২০শে জুন, ১৮৫৭]
এই ছিলো হিন্দুদের মনোভাব!
স্বাধীনতা সংগ্রামী মুসলমানদেরকে হিন্দু পত্রিকাগুলো কোন দৃষ্টিতে দেখতো এবং বন্দী স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতি কি ধরনের নিষ্ঠুর মনোভাব প্রকাশ করতো তা নিচের আর একটি উদ্ধৃতি থেকেই সহজে অনুমান করা যায়।
আঠারো শো সাতান্ন সালের আঠারো ও বিশে জুনের ‘সংবাদ ভাস্কর’-এ আবারও লেখা হয়:
“আগ্রা, দিল্লী, কানপুর, অযোধ্যা, লাহোর প্রদেশীয় ভাস্কর পাঠক মহাশয়েরা এই বিষয়ে মনোযোগ করিবেন এবং পাঠ করিয়া বিদ্রোহীদের আড্ডায় ইহা রাষ্ট্র করিবেন এবং পাঠ করিয়া বিদ্রোহীদের আড্ডায় আড্ডায় ইহা রাষ্ট্র করিয়া দিবেন, সিপাহীরা জানুক বৃটিশ গভর্নমেন্ট সিপাহী ধরা আরম্ভ করিয়াছেন, আর বিদ্রোহী সকল শোন্ শোন্, তোদের সর্বনাশ উপস্থিত হইল, যদি কল্যাণ চাহিস তবে এখনও বৃটিশ পদান হইয়া প্রার্থনা কর-ক্ষমা করুন।.. গত বুধবার বেলা দুই প্রহর, ঘন্টাকালে সৈন্য পরিপূর্ণ এক জাহাজ উত্তর দিক হইতে আসিয়িা কলিকাতা দুর্গের দক্ষিণাংশে লাগিল। সে সময় উক্ত জাহাজ অতি সুদৃশ্য দৃষ্ট হইল, গোরা সৈন্যরা পাঁচশ’ সিপাহীকে হাতে হাতকড়ী পায়ে পবেড়ী দিয়া লইয়া আসিয়াছে, গভর্ণমেন্ট সিপাহীদিগের প্রতি যে প্রকার ক্রোধ করিয়া রহিয়াছেন, তাহাতে বলিদান দিনে ইহাই জ্ঞানগ্রাহ্য হইতেছে। কালিঘাটে বহুকাল নরবলি হয় নাই। আমাদিগের রাজেশ্বর যদি হিন্দু হিইতেন, তবে এই সকল নরবলি দ্বারা জগদম্বার তৃপ্তি করিতেন।”
অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় বটে!
তবুও এটাই সত্য যে, হিন্দুরা কখনই ইসলামী আন্দোলন ও স্বাধীনতা- সংগ্রামকে সুনজরে দেখেনি।
বরং এর তীব্র বিরোধিকা করেছে প্রতিটি পদক্ষেপে।
আশার কথা, তবুও থেমে থাকেনি হাজী শরীয়তুল্লাহসহ মর্দে মুজাহিদদের সংগ্রাম। দুর্বার আন্দোলনের ক্রমধারা!
একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য
ভারতীয় রাজনীতি পর্যালোচনা করতে গিয়ে স্যার উইলিয়াম হান্টার আঠারো শো একাত্তর সালে লেখেন,
“এতে কোনো সন্দেহ নেই যে ভারত গভর্নমেন্ট যদি পূর্ব থেকেই ষড়যন্ত্র আইনের ৩ নং ধারা অনুযায়ী ভারতের আলেমদের কঠোর হস্তে শাসন করতো, তাহলে ভারত গভর্নমেন্টকে মুজাহিদ আলেমদের আক্রমণের ফলে এত দুঃখ ভোগ করতে হতো না। কতিপয় আলেমকে গ্রেফতার হতো না এবং লক্ষ লক্ষ পাউন্ড বেঁচে যেত। এমন কি উক্ত লড়াই-এর পরও যদি কঠোর হস্তে আলেমদেরকে দমন করা হতো তবে অন্ততপক্ষে ১৮৬৮ খৃস্টাব্দে কালাপাহাড় অভিযান হতে রক্ষা পাওয়ার আশা ছিল।”
উইলিয়াম হান্টর এখানে আলেমদের কঠোর হস্তে দমন না করায় দুঃখ ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছন!
কিন্তু প্রকৃত সত্য হলো, ইংরেজরা তাদের সাধ্যানুসারে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে এমন কোনো কঠোর পদক্ষেপ নিতে বাদ রাখেনি।
ফকির বিদ্রোহকে তারা কঠোর হাতেই দমন করেছিলো!
তিতুমীর ও হাজী শরীয়তুল্লাহর সংগ্রামকেও দমন করার জন্যে ইংরেজরা সকল প্রকার জুলুম নির্যাতন চালিয়েছিলো!
সংগ্রামরত মুসলমানদের প্রতি ইংরেজরা ছিলো বরাবরই কঠোর ও নির্মম!
সমগ্র ভারত বর্ষ বিস্তৃত সাইয়েদ আহমদ বেরেলভীর স্বাধীনতা সংগ্রামকেও শত রকম নির্যাতনের মাধ্যমে তারা প্রতিহত করার চেষ্টা করেছিলো।
ইংরেজদের শত বাধা এবং হিন্দুদের হাজার চেষ্টাতেও এ উপমহাদেশের সংগ্রামরত বীর মুজাহিদদের আন্দোলন কখনো থেমে থাকেনি।তাদের রক্ত-চক্ষুকে উপেক্ষা করে সর্বদা এগিয়ে গেছেন সকল সাহসী সৈনিক! এই সাহসী সৈনিকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন হাজী হাজী শরীয়তুল্লাহ।
আমৃত্যু তিনি লড়ে গেছেন একজন প্রকৃত সৈনিকের মতো!
লড়ে গেছেন সত্যের পক্ষে এবং মিথ্যার বিরুদ্ধে।
ইতিহাসের পুনর্পাঠ
২৮শে জানুয়ারী ১৯৯৯ সাল।
এই দিনে বাংলাদেশের একটি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ করলো হাজী শরীয়তুল্লাহর ওপর একটি সংখ্যা।
যেটা ছিলো ব্যতিক্রম এবং অভিনন্দনযোগ্য।
মূল শিরোনামছিলো- “বাংলাদেশের জাতীয় জাগরণের অন্যতম পথিকৃত ঐতিহাসিক ফরায়েজী আন্দোলনের স্থপতি মহান স্বাধীনতা সংগ্রামী হাজী শরীয়তুল্লাহর ১৫৯তম মৃত্যু বার্ষিকী বিশেষ সংখ্যা।”
এই বিশেষ সংখ্যায় দু’টি গুরুত্বপূর্ণ লেখা প্রকাশিত হয়।
প্রথমটির লেখক অধ্যাপক আবদুল গফুর। শিরোনাম- “হাজী শরীয়তুল্লাহ এবং বৃটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রাম।”
দ্বিতীয়টি লেখক মুন্শী আবদুল মান্নান। তাঁর শিরোনাম ছিল- “ফরায়েজী আন্দোলন : তার পটভূমি ও লক্ষ্য।”
খুবই প্রসঙ্গিক হওয়ায় গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে প্রবন্ধ দু’টির অংশবিশেষ এখানে সংযুক্ত করা হলো।
অধ্যাপক আবদুল গফুর তাঁর প্রবন্ধে উল্লেখ করেন:
“আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে হাজী শরীয়তুল্লাহ লাল হরফে লিখে রাখার মত একটি নাম।
হাজী শরীয়তুল্লাহর নামের সাথে জড়িয়ে আছে ফরায়েজী আন্দোলন নারেম একটি সংস্কার আন্দোলনের ইতিহাস।
ফরায়েজী আন্দোলণ পাঠকদের কাছে পরিচিত হয়ে আছে একটি ধর্মীয়, সামাজিক সংস্কার আন্দোলন হিসেবে।
তার প্রতিষ্ঠাতা স্বাধীনতা সংগ্রামে ভূমিকা রাখেন কি করে, এ প্রশ্ন উত্থাপিত হওয়া খুবই স্বাভাবিক।
এ প্রশ্নের জওয়াব পেতে হলে আমাদের ফরায়েজী আন্দোলনের প্রকৃতি ও পটভূমির দিকে সন্ধানী দৃষ্টিতে তাকাতে হবে।
হাজী শরীয়তুল্লাহকে আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ হিসেবে মেনে নিলেও তাঁর হাতে যে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম সূচনা হয়নি, এটাও এক ঐতিহাসিক সত্য।
অবিশ্বাস্য হলেও সত্য এই যে, ১৭৫৭ সালের পলাশীতে আমাদের স্বাধীনতা হারাবার মাত্র আট বছরের মাথায় ১৭৬৪ সালে আমাদের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার সংগ্রামের সূচনা করেন এমন এক ব্যক্তি, যিনি পলাশী ষড়যন্ত্রেরও অন্যতম সহযোগী ছিলেন।
তিনি মীর জাফর আলী খাঁর জামাতা মীর কাসিম আলী।
ইংরেজরা মীর জাফরকে সরিয়ে মীর কাসিমকে নবাব করার অল্পদিন পরই তিনি ইংরেজ আধিপত্যের বিরুদ্ধে প্রথম সংঘাতে, পরে সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত হন।
কিন্তু ধনুক থেকে একবার তীর ছোঁড়া হয়ে গেলে তা যেমন ফিরে আসে না, মীর কাসিমের এ স্বাধীনতা সংগ্রামও তেমনি স্বাভবিক কারণেই ব্যর্থ হয় এবং স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার সংগ্রাম শুরুর দায়ে তাকে করুণ মৃত্যুবরণ করতে হয়।
মীর কাসিমের প্রায় সমসাময়িক কালেই মজু শাহের নেতৃত্বে উত্তরবঙ্গে আরেকটি স্বাধীনতা সংগ্রাম সূচিত হতে দেখা যায়।
ইতিহাসে এটি ফকির আন্দোলন রূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।
১৭৬৩ সালে ফকির বাহিনী ঢাকায় ইস্ট কোম্পানীর কুঠির ওপর প্রথম আক্রমণ পরিচালনা করেন।
ইংরেজদের হাতে পর্যুদস্ত রণক্লান্ত মীর কাসিম ১৭৭৭ সালে অসহায়ভাবে ইন্তেকাল করেন।
কিন্তু ফকির মজনু শাহের সূচিত ফকির আন্দোলন ১৭৮৭ সাল তাঁর মৃত্যুর পরও বহুদিন পর্যন্ত জারি ছিল।
মজনু শাহের মৃত্যুর পর তাঁর ভাই মুসা শাহ ফকির আন্দোলনের নেতা হন। ১৭৯১ পর্যন্ত মুসা শাহ ও তাঁর অন্যতম সহযোগী চেরাগ আলী যে রংপুর ও ময়মনসিংহ এলকায় সক্রিয় ছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায়।
তবে ফকিররা প্রধানত ইংরেজদের এবং তাদের আশীর্বাদপুষ্ট জমিদারদের ওপর আচমকা আক্রমণ চালিয়ে তাদের জানমালের ক্ষয়ক্ষতি সাধনের বাইরে স্বাধীনতা আন্দোলনে কোনো সুপরিকল্পিত সাংগঠনিক কর্মসূচী নিয়ে অগ্রসর হননি বলে এ আন্দোলনকেও আঠার শতকের শেষাশেষি স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করে।
স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে ফরায়েজী আন্দোলনের গুরুত্ব অনুধাবন করতে হলে আমাদের অবশ্য এর পটভূমি এবং এর প্রতিষ্ঠানের জীবন, কর্ম ও চিন্তাধারাকে সূক্ষ্মভাবে পর্যালোচনা করতে হবে।...
হাজী শরীয়তুল্লাহ মক্কায় যান ১৭৯৯সালে এবং সেখানে একটানা ২০ বছর কাটিয়ে ১৮১৮ সালে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন।
এই দীর্ঘ সময়কাল তিনি কাটান ধর্মীয় অধ্যয়ন ও সাধনায়।
আরব দেশে তখন মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওহাব [১৮০৩-৯২] পরিচালত ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের জোয়ার চলছে।
তিনি এ আন্দোলনের সংস্পর্শে এসে মুসলিম সমাজে শিরক, বিদয়াত প্রভৃতি অবাঞ্ছিত ইসলাম বিরোধী কুসংস্কারের অনুপ্রবেশ সম্পর্কে সচেতনতা লাভ করলেও ঐ আন্দোলনের সাথে যোগ দেননি।
কারণ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওহাবের সূচিত আন্দোলনের মাযহাব বিরোধিতা তাঁর মনঃপুত হয়নি।
বাংলাদেশের অধিকাংশ মুসলমান মাযহাব হানাফী মাযহাব বাদ দিয়ে হাম্বলী মাযহাবে দাখিল হওয়ার কোন জরুরত তিনি অনুভব করেননি।
তিনি মক্কা শরীফেও একাধিক হানাফী আলেম ও বুজুর্গের কাছে ইসলাম সম্পর্কে উচ্চতর শিক্ষা লাভ করেন।
দুই বছর তিনি কায়রোর আল-আজহারে শিক্ষা লাভকরেন।
আরব দেশে দীর্ঘকাল অবস্থান এবং ধর্ম সম্পর্কে গভীর অধ্যয়ন ও গবেষণার পর তিনি যে স্বপ্ন স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন পরাধীন দেশবাসীর করুণ অবস্থা দেখে তাঁর সে স্বপ্ন অনেকাংশেই উবে যেতে চাইলো। হাজী শরীয়তুল্লাহ দেখলেন, তাঁর দেশবাসী যেন শুধু রাজনেতিক ভাবেই গোলামীর শিকরে বাঁধা পড়িন, ধর্মীয়, সামাজিক,সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়েও স্বাধীন স্বতন্ত্র সত্তা হারিয়ে বসে আছে।
স্বাধীনতা হারানোর ছয় দশকের মধ্যেই তাদের এ করুণ অবস্থা দেখে তাঁর মন বেদনার্ত হয়ে উঠলো।
তিনি দেখলেন পৃথিবীতে যে ইসলাম এসেছিল মানুষকে জীবনের সর্বপর্যায়ে স্বাধীনভাবে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর শিক্ষা দিতে, সেই ইসলামের অনুসারী হয়েও তাঁর স্বদেশবাসী অধঃপতনের নিম্নতম পর্যায়ে নেমে গেছ।
তাদের চোখের সামনে ইসলামের সে বিপ্লবী রূপের সামান্যতম ছবিও আর উপস্থিত নেই।
ইসলামের কালেমা এসেছিল ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’... এক আল্লাহ ছাড়া মানুষের আর কোনো প্রভু নেই- এই বিপ্লবী আদর্শ শিক্ষা দিতে।
অথচ তার স্বজাতির মধ্যে চলছে অসংখ্য নকল খোদার দাপট আর প্রবুত্ব।
ইসলাম এসেছিল দুনিয়ায় তৌহিদের আদর্শ এক আল্লাহর বন্দেগী বা আনুগত্য শিক্ষা দিতে।
অথচ শরীয়তুল্লাহ দেখলেন, তাঁর সমাজের লোকেরা এক আল্লাহর ইবাদাতের স্থলে পীর পূজা, কবর পূজা, ইংরেজ পূজা, জমিদার পূজা, মহাজন পূজার মাধ্যমে অসংখ্য নকল খোদার পূজায় লিপ্ত রয়েছে।
মুসলিম শাসনামলেও যে সমাজের সর্বস্তরে ইসলামের বিধান পুরোমাত্রায় চালু ছিল, তা হয়ত নয়।
তবুও মানুষের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা তখন অনেকটাই সমুন্নত ছিল।
ফলে হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সকলের নিজ নিজ ধর্মীয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক জীবনে পর্যাপ্ত স্বাধীনতা ও সমৃদ্ধি ছিল।
সোনার বাংলার সেদিনের সেই সমৃদ্ধি সম্পদের লোভেই সাত সমুদ্রের ওপর থেকে এসে বণিকবেশী ইংরেজরা ষড়যন্ত্র পাকিয়েছিল এদেশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে।
পলাশীর ষড়যন্ত্রে ইংরেজদের সাথে হাত মিলিয়ে জগৎশেঠ, রাজবল্লভ, রায়দুর্ভল ও উমিচাঁদেরা এদেশে মুসলিম শাসন উৎকাতে সাহায্য করার পারিতোষিক ঠিকই পেয়েছিল সুদে-আসলে।
পলাশী যুদ্ধের আট বছরের মধেই আশি হাজার মুসলমান সেনাবাহনিী থেকে বরখাস্ত হয়।
একে একে সমস্ত মুসলমান আমীর-ওমরাহকে সরকারী পদ থেকে অপসারিত করে সেখানে ইংরেজভুক্ত হিন্দুদের নিয়োগ করা হয়।
বেছে বেছে মুসলমান আয়মদার, জায়গীরদার উৎখাত করে সেখানে ইংরেজ খয়ের খাঁ হিন্দুদের বসানো হয়।
মুসলিম শাসনামলে জমিদাররা কখনও জমির মালিক ছিল না, জমির প্রকৃত মালিক ছিল কৃষকরা, জমিদাররা শুধু নির্দিষ্ট মেয়াদে রাজস্ব আদায় করত। ১৭৯৩ সালে সে ব্যবস্থা রহিত করে কৃষকদের মাথার ওপরে জমিদারদের জমির চিরস্থায়ী মালিক করে বসিয়ে দেয়া হল।
বলাবাহুল্য এই নতুন জমিদারদের প্রায় সবাই ছিল হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত।
এরা কৃষকদের ওপর করের পর কর বসিয়ে তাদের জীবনকে অতিষ্ঠ করে তুললো।
জমিদারের ছেলে মেয়েদের বিবাহ ও নানা পার্বণ উপলক্ষে প্রজাদের কাছ থেকে কর আদায় করা হতে লাগলো।
মুসলমান প্রজাদের ওপর অতিরিক্ত থাকত দাড়ির ট্যাক্স এবং আজান ও গরু কুরবানির ওপর নিষেধাজ্ঞার মত জঘন্য অত্যাচার।
একদিকে জমিদারদের জুলুম, নির্যাতন, অন্যদিকে নব্য ধনিক হিন্দু মহাজনদের কুমিদ ব্যবসা- দুইযে মিলে গ্রামের সাধারণ মানুষ, বিশেষকরে মুসলমানদের জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠেছিল।
মুসলিম শাসনামলের যে মসলিন বস্ত্র-শিল্প একদা সারা বিশ্বে খ্যাতি অর্জন করেছিল, তাকে ধ্বংস করে দেয়ার জন্য মসলিন শিল্পীদের হাতের আঙ্গুল কেটে ফেলার মত নৃশংসতা প্রদর্শনেও ইংরেজদের দ্বিধা হয়নি।
পলাশী বিপর্যয়ের পর মুর্শিদাবাদসহ বাংলার সম্পদ লুন্ঠনের মাধ্যমে ইংল্যান্ড নতুন করে সমৃদ্ধি নির্মাণের পালা শুরু হয়, যার ফলে সেদেশে শিল্প বিপ্লব সম্ভব হয়।
ইংল্যান্ডের বস্ত্র-শিল্পের জন্য জায়গা করে দিতে এদেশের উন্নত বস্ত্র-শিল্পই শুধু ধ্বংস করা হল না, কৃষকদের অর্থনৈতিক মেরুদন্ড অর্থকারী ফসলের স্থলে নীলচাষেকৃষকদের বাধ্য করা হতে লাগলো।
বিদেশী শাসক এবং তাদের এতদ্দেশীয় দালালদের মিলিত ষড়যন্ত্রের ফলে- যে দেশে মুসলিম শাসনের ৫০০ বছরে কোনো দুর্ভিক্ষহয়নি, পলাশী বিপর্যয়ের মাত্র দুই দশকের মধ্যেই ছিয়াত্তরের দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। এই ভয়াবহ দুর্ভিক্ষে কুকুর-বিড়ালের মত প্রাণ হারালো এদেশের লাখ কোটি বনি আদম।
একদিকে এদেশের জনগণের করুণ অবস্থা, অন্যদিকে শিক্ষা-দীক্ষা, অর্থনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, ধর্ম-সংস্কৃতি সকল দিকে মুসলমানদের অসহায়তা পর্যায়ে।
মুসলমানদের ভুলিয়ে দেয়া হয়েছিল তাদের সুমহান সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের কথা।
তারা হিন্দুদের অনুকরণে বসন্ত রোগে শীতলা দেবীর পূজা, সর্প দংশনে মজমা পূজা প্রভৃতিতে লিপ্ত হতে লাগলো বিনা দ্বিধায়।
অন্যান্য পূজায় সরাসরি অংশ না নিলেও পূজা-পার্বনে চাঁদা দেয়া ও নৈবেদ্য ভক্ষণে অংশগ্রহণ নিজেদের দায়িত্বের অন্তর্গত করে নিয়েছিল।
তারা শিশুর নাম রাখতে লাগল হিন্দুদের অনুকরণে।
হজ্ব, যাকাত তো আগেই ভুলেছিল, নামায-রোযাও আস্তে আস্তে ভুলে যেতে লাগল।
একদিকে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এসব বিচ্যুতি, অন্যদিকে ইসলামের সামাজিক সাম্য, ভ্রাতৃত্বের কথা ভুলে গিয়ে হিন্দুদের কুলীণ-অকুলীন, বড়জাত-ছোটজাতের ভেদ বৈষম্যের অনুকরণে বিভক্ত করে ফেললো।
শ্রেণীতে নিজেদের বিভক্ত করে ফেললো। রাসূল [সা] যেখানে বলেছেন, পরিশ্রমের মাধ্যমে জীবিকা অর্জনকারী আল্লাহর বন্ধু, সেখানে কৃষকদের ‘চাষা’, তাঁতীদের ‘জোলা’ বলে তাদের নীচু জাতের মানুষ ভাবতে শুরু করলো মুসলমানরা।
ইসলামেযে বলা হয়েছিল- বর্ণ, রক্ত, বংশ, গোত্র বা পেশার ভিত্তিতে নয়,একমাত্র ধর্মনিষ্ঠা তথা তাকওয়ার ভিত্তিতেইইসলামে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব নির্ধারত হয়, সেই শিক্ষা এভাবেই মুসলমানরা ভুলে গিয়েছিল।
হাজী শরীয়তুল্লাহ শুধু ইসলাম সম্পর্কে অধ্যয়নই করেননি, স্বদেশে ও স্বজাতির এই দুঃজনক অবস্থার কারণে নিয়েও যথেষ্ট পড়াশুনা ও চিন্তাভাবনা করেন গভীরভাবে।
স্বদেশে ও স্বজাতির এই চরম দুরবস্থার প্রধান কারণ যে পরাধীনতার প্রভাব, এ সম্বন্ধে তাঁর মনে কোনই সন্দেহ ছিল না।
কিন্তু স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের জন্য মুসলমানদের যে প্রস্তুতি প্রয়োজন, সচেতনতা অপরিহার্য তার কোনো লক্ষণই মুসলিম সমাজে তিনি দেখতে পেলেন না।
এমনকি ইসলামের অনুসারী কোনো জনগোষ্ঠী যে কোনো পর্যায়েই আল্লাহ ছাড়া কারো গোলামীকে মেনে নিতে পারে না- সেই চেতনা, সেই অনুভূতি কোথায়?
শুধু স্বাধীনতার কথা বললেই তো আর হবে না!
মীর কাসেম ও মজনু শাহদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ব্যরথতার ইতিহাস হাজী শরীয়তুল্লাহর সামনেছিল।
তাই জাতির মন-মানসিকতার ক্ষেত্রে স্বাধীনতার ভিত রচনার লক্ষ্যে তাদের মধ্যে প্রথমে একটি স্বাধীনতাকামী জাতি হিসেবে কর্বত্য সচেতনতা সৃস্টির সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য নিয়ে তিনি কাজে নামলেন।
হাজী শরীয়তুল্লাহ জাতির স্বাধীনতাকে চূড়ান্ত লক্ষ্য হিসেবে রেখে যে সংস্কার আন্দোলনের সূত্রপাত করেন তার নাম- ‘ফরায়েজী আন্দোলন’।... সেদিনের মুসলিম সমাজকি আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে, কি সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক- সকল ক্ষেত্রেই তার আদর্শ হারিয়ে ফেলেছিল।
হারিয়ে ফেলেছিল একটি পূর্ণাঙ্গ আদর্শ ইসলামের আলোকে তার অবশ্য পালনীয় দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতনতা।
এই দায়িত্ব তথা অপরিহার্য কর্তব্য সচেতনতা জাতির মধ্যে সৃষ্টি করতেই তিনি তাঁর আন্দোলনের নাম ‘ফরায়েজী আন্দোলন।’
এই আন্দোলনের মাধ্যমে মুসলমানদের মধ্যে তিনি ধর্মীয়, আধ্যাত্মিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কর্তব্য সচেতনতা সৃষ্টির আহ্বান জানান।
ইসলামে আধ্যাত্মিকতার যে উচ্চস্থান রয়েছে, তা মেনে নিয়েও শরীয়তুল্লাহ সমাজের এক শ্রেণীর ধর্ম ব্যবসায়ীর পীর-মুরিদী ব্যবসাকে নিরুৎসাহিত করার লক্ষ্যে ‘পীর’-‘মুরিদ’ শব্দ দু’টি পরিহার করে তার স্থানে আধ্যাত্মিক শিক্ষককে ‘ওস্তাদ’ ও অনুসারীকে ‘শাগরেদ’ বলে আখ্যায়িত করতে প্রয়াস পান এবং অতীতের ইহুদী নামাবাতের মত ধর্মগুরুদের প্রভু বলে পূজা করার প্রবণতার বিরুদ্ধে সকলকে সাবধান করে দেন।
ইসলামের সামাজিক ক্ষেত্রে সাম্য-ভ্রাতৃত্বের আদর্শের আলোকে হিন্দু কুলীন-অকুলীন প্রথার মত মুসলমান সমাজে আশরাফ-আতরাফ শ্রেণীভেদ সৃষ্টির বিরুদ্ধে তিনি সকলকে সতর্ক করে দেন।
যেহেতু ইসলামে শ্রমের মাধ্যমে জীবিকা অর্জনকারীর অতি উচ্চ মর্যাদা, তাই তাদেরকে চাষা, জোলা প্রভৃতি বলে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করার বিরুদ্ধে তিনি সকলকে হুঁশিয়ার করে দেন এবং সকল স্তরের মানুষের মধ্যে সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও শ্রমের মর্যাদা প্রভৃতি ইসলামী মূল্যবোধ প্রবর্তনের প্রয়াস পান।
মুসলমানদের মধ্যে সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মুসলমানদের মধ্যে যে আচার আচরণ ও অনৈসলামী কুসংস্কার অনুপ্রবেশ করেছিল, সেসব দূর করার জন্যে তিনি আকুল আহবান জানান।
ধর্মীয় আবশ্যিক কর্তব্যাদি যেমন- কালেমা, নামায, রোযা, হজ, যাকাত- এগুলো পালনের পাশাপাশি তিনি মুসলমানদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি এবং অন্যায়-অনাচার প্রতিরোধে তাদেরকে সংঘবদ্ধ করে তোলেন।
শিরক, বিদআত, অনৈসলামী কুসংস্কার ও বিজাতীয় অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে পরিচালিত আদর্শবাদী সংস্কার আন্দোলনে তিনি মুসলমানদের সংঘবদ্ধ করে তোলেন।
তাঁর আন্দোলন যদিও প্রত্যক্ষভাবে সীমাবদ্ধ ছিল ধর্মীয়, আধ্যাত্মিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে- তবুও পরোক্ষভাবে তিনি অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনেরও বুনিয়াদ গড়ে তোলেন।
যার ভিত্তিতে তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর সুযোগ্য পুত্র মুহাম্মদ মহসিন উদ্দিন ওরফে দুদু মিয়া গড়ে তোলেন বিপ্লবী রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক আন্দোলন। দুদু মিয়ার সেই আন্দোলনের ফলে একদিকে বৃটিশশাসকগোষ্ঠী, অপরদিকে তাদের আশীর্বাদপুষ্ট শোষক জমিদার গোষ্ঠীর ভিত্তিমূল পর্যন্ত প্রকম্পিত হয়ে ওঠে।
ফলে, ফরায়েজী আন্দোলনের সেই সিংহপুরুষকে বৃটিশরাজ প্রায় আমৃত্যু কারাগারে শৃংখলিত রাখতে বাধ্য হয়।
হাজী শরীয়তুল্লাহর চূড়ান্ত লক্ষ্য ছিল যে বৃটিশ শাসনের অবসান ঘটিয়ে দেশকে স্বাধীন করে তোলা, তার বড় প্রমাণ- পরাধীন দেশকে ‘দারুল হরব’ [ইসলাম বিরোধী রাষ্ট্র] ঘোষা করে স্বাধীনতা না আসা পর্যন্ত ঈদ ও জুমআর নামায স্থগিত রাখার পক্ষেতাঁর ঘোষণা। দেশের মুসলিম শাসক বা তার প্রতিনিধির উপস্থিতি এখানে অপরিহার্য।
এই দৃষ্টিতে তিনিএ রায় ঘোষণা করেন।
তিনি নিজে ঈদ বা জুমআর ভক্ত ছিলেন না, তা নয়।
স্বাধীনতা সংগ্রামের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিতেই তিনি এ ঘোষণা দিয়েছিলেন। জনগণের মধ্যে স্বাধীনতা সংগ্রামের মন-মানসিকতা সৃষ্টিতে তাঁর ঐতিহাসিক ভূমিকা কোনো মতেই অস্বীকার করা সম্ভব নয়।
হাজী শরীয়তুল্লাহর উত্তরসূরিগণ স্বাধীনতার লক্ষ্যে প্রবর্তিত তাঁর আন্দোলনকে নানা বাধা-বিপত্তির মধ্য দিয়েও যৌক্তিক পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যান।
শরীয়তুল্লাহর পুত্র মুহাম্মদ মহসিন উদ্দিন দুদু মিয়ার সময় ফরায়েজী আন্দোলন শক্তিশালী গণ-আন্দোলনে পরিণত হয়।
দুদু মিয়া তাঁর প্রভাবাধীন এলাকাকে কয়েকটি খণ্ডে বিভক্ত করেন এবং একেক অংশেরজন্য একেকজন খলীফা নিয়োগ করেন।
তার প্রভাবাধীন এলাকায় জনগণের মামলার শালিসের ব্যবস্থা তিনিই করতেন। কোনো মামলা-মোকদ্দমার জন্য ইংরেজদের আদালতে যাওয়ার তিনি নিষেধ করে দেনে।
এদেশে কৃষক আন্দোলনের ভিত্তি রচনা করে তিনি ঘোষণা দেন- জরি মালিক আল্লাহ। সুতরাং চাষীরা তাদের আয়ত্তাধীন জমির খাজনা সরকার বা জমিদারকে দেবে না।
এতে করে স্বাভাবিকভাবেই সরকার ও জমিদারদের সাথে তাঁর সংঘাত এবং সংঘাত থেকে সংঘর্ষ বেধে যায়।
এসব সংঘর্ষ-সংঘাতের শেষ পরিণতিতে সরকার তাঁকে দীর্ঘদিন কারারুদ্ধ করেরাখে।
দীর্ঘ কারা ভোগের ফলে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং কারাগার থেকে মুক্তি লাভের অল্পদিন পরেই তিনি ইন্তিকাল করেন।
দুদু মিয়ার মৃত্যুর পর তাঁর তিন পুত্র গাজী উদ্দিন হায়দার [১৮৬২-৬৪], আব্দুল গফুর ওরফে নয়া মিয়া [১৮৬৪-৮৩] এবং খান বাহাদুর মাইনউদ্দিন আহমদ [১৮৮৩-১৯০৬] যথাক্রমে ফরায়েজী আন্দোলনের নেতা মনোনীত হন।
শেষোক্ত মাইনউদ্দিন আহমদ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন সমর্থন করেন। সাইফুদ্দিনের পর তাঁর পুত্র আবু খালেক রশিদ উদ্দিন ওরফে বাদশা মিয়া ফরায়েজীদের ওস্তাদ মনোনীত হন।
তিনি খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারাবরণ করেন।
জীবনের শেষপ্রান্তে তিনি পাকিস্তান আন্দোলনে যোগ দেন।
বাদশা মিয়া ১৯৫১ সালের ১৩ ডিসেম্বর ইন্তিকাল করেন।
১৯৪৭ সালে বৃটিশ শাসনের অবসান ও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর তিনি তাঁর অনুসারীদের ঈদের নামায আদায়ের অনুমতি দেন।”
মুন্শী আবদুল মান্নান তার প্রবন্ধে উল্লেখ করেন-
“পলাশী বিপর্যয়ের [১৭৫৭ সালের ২৩শে জুন] মধ্য দিয়ে কার্যত বাংলার মুসলিম শাসনের অবসান সূচিত হয়।
পরবর্তীতে নামকাওয়াস্ত কয়েকজন নবাবের আবির্ভাব ঘটলেও এরা সবাই ছিলেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর হাতের ক্রীড়নক মাত্র।
এদের মধ্যে একমাত্র নবাব মীর কাসিমই উপলব্ধি করতে পারেন যে, বাংলার এত দিনের মুসলিম শাসন মারাত্মকভাবে বিপন্ন হয়ে পড়ছে।
তিনি পলাশী ট্রাজেডির আট বছরের মধ্যে অর্থাৎ ১৭৬৪ সালে স্বাধীনতা সুরক্ষা বা পুনরুদ্ধারের জন্য কোম্পানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন।
‘বক্সারের যুদ্ধ’ নামে পরিচিত এই যুদ্ধে তাঁর শোচনীয় পরাজয় ঘটে।
ঐতিহাসিকদের মতে, এটা পরাজয়ের মধ্য দিয়ে প্রকৃত ক্ষমতা ও পূর্ণ কর্তৃত্ব কোম্পানীর হাতে চলে যায়।
রাজনৈতিক ক্ষমতাও তাদের করতলে চলে গিয়েছিল।
১৭৬৫ সালে দেওয়ানী গ্রহণের মধ্য দিয়ে নিরংকুশ ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অধিকারী হয়ে যায় কোম্পানী।
এই পরিবর্তনের ফলে কেবল স্বাধীন নবাব বিদেশীদের শাসনে আবদ্ধ হলেন না, একই সাথে শাসক মুসলমান শাসিতের শ্রেণীতে পরিণত হয়ে গেল।
যেহেতু মুসলমানদের হাত থেকেই ক্ষমতা ছিনিয়ে নেয়া হয়, সুতরাং মুসলমানরাই নব্য শাসকদের সর্বপ্রকার অন্যায়, জুলূম, পীড়ন ও শোষণের শিকারে পরিণত হয়।
কোম্পানী মুসলমানদের রাজনৈতিক, সামরিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে উৎখাত করার দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হয় এবং একে একে এই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে।
প্রথমেই নব্য শাসকরা দ্বিমুখী নীতি গ্রহণ করে।
মুসলমানদের সরারী বা রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ পদ থেকে সরিয়ে দেয়।
তাদের স্থলে প্রতিবেশী হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকদের নিয়োগ করে।
অর্থনৈতিক ও অন্যান্য ক্ষেত্রে এদের সুযোগ-সুবিধা দিয়ে পুরোপুরি নিজেদের দলে ভিড়িয়ে নেয়।
লাখেরাজ ও আয়মা সম্পত্তি থেকে মুসলিমদের বঞ্চিত করা হয়।
বিভিন্ন প্রকার নিপীড়নমূলক কর তাদের ওপর ধার্য করা হয়।
সরকার ও সেনাবাহিনী থেকে মুসলমানদের অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে সরিয়ে দেয়া হয়।
এক হিসাব থেকে দেখা যায়, ১৭৫৭ থেকে ১৭৬৫ সালের মধ্যে কেবল সামরিক বাহিনী থেকেই ৮০ হাজার মুসলমানকে তাড়িয়ে দেয়া হয়।
১৭৫৭ সালের পট পরিবর্তনেরপর সর্বব্যাপী এমন এক শোষণ, পীড়ন ও নাশকতার উদ্ভব ঘটে যে, ১২ বছরের মাথায় স্মরণকালের সবচেয়ে বিভীষিকাময় দুর্ভিক্ষ নেমে আসে গোট বাংলায়।
ইতিহাসে ছিয়াত্তরের [বাংলা ১১৭৬ সন] মন্বন্তর নামে চিহ্নিত এই মহাদুর্ভিক্ষে লাখ লাখ মানুষের খাদ্যাভাবে অসহায় মৃত্যু ঘটে।
জমিদারের খাজনা, নীলকরদের অমানুষক নির্যাতন, মহাজনের দেনার চাপ এবং শাসকদের শোষণ-শাসন-পড়নে যখন জনগণ বিপন্ন ও দিশাহারা ঠিক তখনই এই মন্বন্তর আঘাত হেনে গোটা বাংলাকে প্রায় গোরস্তানে পরিণত করে।
এরপর ১৭৭২ থেকে ১৭৭৩ সালের মধ্যে কোম্পানী যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চাপিয়ে দেয়, তা ‘মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা’ হয়ে দাঁড়ায়।
১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের ফলে ভূীম ব্যবস্থায় যে পরিবর্তন ঘটে, তাতে বাংলার কৃষক সাজ বস্তুত ভূমিদাসে পরিণত হয় এবং কৃষক সমাজের অর্থনৈতিক অবস্থা পুরোপুরি ভেঙ্গে পড়ে।
অপরদিকে মুসলিম জমিদার তালুকদাররা জমিদারী-তালুকদারী হারিয়ে সর্বস্বহীন হয়ে পড়ে এবং তাদের জমিদারী-তালুকদারী তাদেরই নামের গোমস্তারা হস্তগত করে নেয়।
এদের অধিকাংশই ছিল কোম্পানীর সহযোগী-সহায়তাকারী হিন্দু সমাজের অন্তর্গত।
শুধু তাই নয়, ডাকাত-দস্যুরা পর্যন্ত কোম্পানীর শাসকদের অনুকুল্যে রাতারাতি ‘রাজা’ মহারাজা’ বনে যায়।
দস্যু দলপতি দেবী সিংয়ের ‘রাজা’ হওয়ার কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়।
দেবী সিংহ শুরুতে খাজনা আদারে ইজারাদারী লাভ করে।
দুর্ভিক্ষের সময় খাজনা আদায়ের নামে এই দেবী সিং উত্তরবঙ্গের কৃষকদের ওপর এমন নিপীড়ন ও অত্যাচার চালায় যে, হাজার গ্রাম জনশূন্য হয়ে পড়ে।
পরবর্তীতে দেবী সিং রাজা উপাধি পায় এবং বিরাট জমিদারী পত্তন করে। বাংলা কৃষিনির্ভর আর্থ-সামাজিক কাঠামোর ওপর দাঁড়িয়ে থাকলেও শিল্পক্ষেত্রে পিছিয়ে ছিল না।
সমকালীন বিশ্বে শিল্পক্ষেত্রে বাংলার বিশিষ্ট স্থান ও অবস্থান ছিল।
সেই সময় ঢাকাই মসলিনের খ্যাতি ছিল বিশ্বজোড়া।
বস্ত্র ছাড়াও বিভিন্ন পণ্য রফতানী করে বাংলা প্রতি বছর বিপুল বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতেন।
শাসকগোষ্ঠী নানা কৌশল ও ষড়যন্ত্র করে এই শিল্পকেও ধ্বংস করে দেয়। এক হিসাবে দেখা যায়, ১৭৮৭ সালে কেবল ঢাকা থেকেই ৩০ লাখ টাকার মসলিন ইংল্যান্ডে রফতানী হয়।
মুসলিম ব্যবসায়ী ও শিল্পীদের ওপর অপরিসীম জুলুম, শোষণ ও নির্যাতন চালিয়ে এমন কি শিল্পীদের আঙ্গুল কেটে দিয়ে এই শিল্পের অস্তিত্ব বিরৈা করে দেয়া হয়।
দেখা যায়, কোম্পানী শাসন প্রতিষ্ঠার ৫০ তেকে ৭০ বছরের মধ্যে বাংলার মুসলমান সমাজ, আর্থ, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয়- সকল ক্ষেত্রে পতিত হয়ে পড়েছে।
বিপদ-বিপর্যয়ের তাদের সীমা-পরিসীমা নেই।
তাদের অস্তিত্ব হয়ে পড়েছে মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন।
রাজনৈতিক ও আর্থিক দুরবস্থার সুবাদে বাংলার জনসমাজের নিম্নতম অবস্থানে এসে দাঁড়িয়েছে গরিষ্ঠ সংখ্যার অধিকারী মুসলমানরা।
অনিবার্যভাবে ধর্মীয় সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও তারা দিক-দিশাহীন গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়েছে।
সুদীর্ঘকাল ধরে হিন্দু সমাজ সম্প্রদায়ের পাশাপাশি বসবাস করার কারণেই মুসলমান সম্প্রদায় সমাজের কোন কোন স্তরে বা পর্যায়ে হিন্দু আচার-সংস্কৃতির প্রভাব পড়েছিল।
রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক অবস্থান হারানোর বিপর্যয়ের মধ্যে এই প্রভাব ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করার সুযোগ পায়।
যার ফলে মুসলমানসমাজে শিরক, বিদয়াত ও অনৈসলামিক আচার-প্রথা এমন এক অবস্থায় আধিপত্য বিস্তার করে যে, পৃথক পরিচয়ে মুসলমান চিহ্নিত করাই দুরূহ হয়ে পড়ে।
মুসলমানদের মধ্যে পীর পূজা, মাজার পূজা ব্যাপক প্রচলন ঘটে।
হিন্দুদের ভূত-প্রেত বিশ্বাস তাদের বিশ্বাসেও পরিণত হয়।
হিন্দুদের বিভিন্ন পূজা, যেমন- গো পূজা, শীতলা দেবীর পূজা, মনসা পূজা ইত্যাদি মুসলিম সমাজেও প্রতিষ্ঠা লাভ করে।
হিন্দুদের দুর্গা পূজার আদলে তাজিয়া মিছিল ও তাজিয়া বিসর্জনের প্রথাও প্রচলিত হয়।
অর্থাৎ তৌহিদাবাদী ধর্মীয় সম্প্রদায় হিসেবে মুসলমানদের পরিচয় ও অস্তিত্বে মুছে যাওয়ার পর্যায়ে এসে দাঁড়ায়।
ঠিক এই পটভূমি ও পরিস্থিতিতে ইসলামের অবিনশ্বর জ্যোতিতে উদ্ভাসিত এক মহান ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটে পতিত ও বিলিয়মান এই মুসলিম সমাজে। তাঁর নাম- আল্লামা হাজী শরীয়তুল্লাহ।
তিনি পতিত স্বধর্মীয় সমাজ উদ্ধারে এবং ব্যক্তি পর্যায়ে ও সমাজের সর্বস্তরে মহান ইসলামের আলো ছড়িয়ে দেবার শপথ গ্রহণ করে সংস্কারবাদী আন্দোলনের সূচনা করেন, যার নাম- ‘ফরায়েজী আন্দোলন।’..
হাজী শরীয়তুল্লাহ যথার্থই উপলব্ধি করেন যে, মুসলমানদের এই অধঃপতন, দুর্গতি ও বিপর্যয়েল প্রধান কারণ বিদেশী ও বিধর্মীয় দুঃশাসন।
এই দুঃশাসনের অবসান ঘটিয়ে স্বাধীনতা ও স্বশাসন কায়েম করা ছাড়া দেশ ও দেশবাসীর মুক্তি- বিশেষত মুসলমানদের স্বগৌরবে অস্তিত্বের পুনঃপ্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়।
বিদেশী-বিধর্মীয় শাসন উৎখাতের জন্য ‘জিহাদ’ ছাড়া কোনো বিকল্প নেই। এই উপলব্ধি থেকে তিনি ঘোষণা দেন:
‘এদেশ শত্রু কবলিত রাষ্ট্র।
ইংরেজ ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে অবৈধভাবে দেশ শাসন করছে। সুতরাং তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করে দেশকে স্বাধীন করা জনগণের একটি বৈধ অধিকার এবং এটি দেশবাসীর একটি পবিত্র দায়িত্ব।’
তাঁর এই দু’টি ঘোষণা নির্যাতিত, নিপীড়িত, শোষিত মুসলমানের মধ্যে উদ্দীপনার সৃষ্টি করে।
পক্ষান্তরে শাসক ও জমিদার শ্রেণর মধ্যে বিরাট আশংকা ও উব্দেগ সঞ্চার করে।
ঢাকা জেলার নয়াবড়ী নামক স্থানের কেন্দ্র করে তিনি তাঁর আন্দোলন শুরু করেন।
অল্প কিছুদিনের মধ্যে ঢাকা, পাবনা, বরিশাল, নদীয়া, মোমেনশাহী প্রভৃতি অঞ্চলে এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে।
তিনি গ্রামে গ্রামে গিয়ে কৃষকদের সংগঠিত করেন এবং ইসলারেম ফরজ প্রতিষ্ঠা, বিদেশী-বিধর্মিদের শাসন উৎখাতের এবং জমিদার ও শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানান।
জনগণ পর্যায়ে- বিশেষত কৃষক তাঁতী সম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁর আন্দোলন ব্যপকভাবে বিস্তার লাভ করে।
তিনি তাদের পথ প্রদর্শক ও অবিসংবাদী নেতায় পরিণত হন।
হাজী শরীয়তুল্লাহ দেশকে ‘দারুল হরব’ বা জিহাদের মাধ্যমে এই শত্রু শাসনউৎখাত করে দেশকে ‘দারুল ইসলাম’ বা ইসলামের আলোয় হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার স্বপ্ন দেখেছিলেন এবং এই স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্যে তাঁর আন্দোলন ছিল উড়ে এসে জুড়ে বসা কোম্পানী শাসকদের বিরুদ্ধে এবং জমিদার মহাজনদের বিরুদ্ধে।
ফলে তারাই যুগপৎভাবে তাঁর বিরুদ্ধে সকল শক্তি নিয়োজিত করেছিল।
কিভাবে হাজী শরীয়তুল্লাহকে সরানো যায়, কেমন করে তাঁকে শায়েস্তা করা যায়- এসব চিন্তা-ভাবনা ও ষড়যন্ত্র একই সাথে চলতে থাকে।
এই পর্যায়ে যখন নয়াবাড়ীর জমিদার ও স্থানীয জোতদারদের সাতে হাজী শরীয়তুল্লাহর সরাসরি বিরোধ দেখা যেদয়, তখন তাঁকে গ্রেফতার করা হয় এবং পরে নয়াবাড়ী থেকে বিতাড়িত করা হয়।
তিনি তাঁর সূচিত আন্দোলনের পূর্ণ সাফল্য দেখে যেতে পারেননি।
১৮৪০ সালে মাত্র ৫৯ বছর বয়সে এই মর্দে মুজাহিদ, কৃষক বন্ধু, স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্রসাধক এবং দারুল ইসলাম প্রতিষ্ঠার স্বপ্নদ্রষ্টা ইন্তিকাল করন।
পরবর্তীকালে ফরায়েজী আন্দোলনের নেতৃত্ব দান করেন তাঁর সযোগ্য পুত্র মোহসিন উদ্দিন।
সিপাহী বিদ্রোহ পর্যন্ত এই আন্দোলন প্রবলভাবে অব্যাহত থাকে।”
এই দুটি পুনর্মূল্যায়নই আমাদের ইতিহাসের জন্য যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি গুরুত্বপূর্ণ হাজী শরীয়তুল্লাহকে জানা ও বুঝার ক্ষেত্রেও।
হাজী শরীয়তুল্লাহ এবং তাঁর সংগ্রামী জীবন যে কত বিশাল-ব্যাপক ছিল, তার তুলনা তিনি নিজেই।
তার সেই বিশাল ভূমিকা ও ইতিহাস আমাদের সাহস ও উদ্দীপনা সৃষ্টির জন্য বার বার সামনে মেলে ধরা প্রয়োজন।
কেননা ৩৮ বছর বয়সে হাজী শরীয়তুল্লাহ তাঁর ফরায়েজী আন্দোলন শুরু করেছিলেন।
সারা জীবন তিনি এখানকার মানুষের মুক্তির সংগ্রামই করে গেছেন।
ফরায়েজী আন্দোলন শুধু ধর্মীয়রূপেই ছিল না, সেই সাথে এটা ছিল আর্থ-সামাজিক ও সংস্কার আন্দোলন।
ইসলামই ছিল এখানে প্রধান ভূমিকায়।
ইসলাম যে কোনো ধরনের অত্যাচারের বিরুদ্ধে এবং শোষিত জনগণের পাশে থাকে, তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্তই রেখেছিলেন হাজী শরীয়তুল্লাহ!
সেই আদর্শই পরবর্তীকালে আরো বিকশিত হয়েছে।
ইন্তিকাল
হাজী শরীয়তুল্লাহ ছিলেন বাংলার মুসলমানদের জন্যে এক সাহসী পুরুষ! তাঁর সমগ্র জীবনটাই ছিলো সংগ্রামের এক দীপ্তশিখা।
তিনি ছিলেন মুসলমানদের জন্যে, সেই চরম দুঃসময়ে একজন নির্ভরযোগ্য অভিভাবক।
ছিলেন সত্যের সৈনিক।
তাঁর হৃদয়ে ছিলো ইসলামের জন্যে অফুরন্ত ভালোবাসা।
অঢেল প্রেম ছিলো তাঁর দেশের জন্যে।
মানুষের জন্যে।
আর তাই তাদেরকে আঁধার থেকে আলোয় আনার জন্যে হাজী শরীয়তুল্লাহ সারাটি জীবন অপ্রাণ চেষ্টা করে গেছেন।
আঠারো শো চল্লিশ সাল।
দিনটি ছিলো আঠাশে জানুয়ারী।
দীর্ঘ সংগ্রামী জীবনের অবসান ঘটিয়ে এই বছর বিদায় নিলেন বাংলার প্রাণপ্রিয় নেতা, ইসলামী আন্দোলনের এক নির্ভীক ও নিবেদিত মুজাহিদ - হাজী শরীয়তুল্লাহ।
ইন্তিকালের পর তাঁর প্রিয় জন্মভূমি ফরিদপুরের শামাইলে ঘুমিয়ে আছেন তিনি।
সত্যিই কি ঘুমিয়ে আছেন?
না! এইতো শত বছর পরও আমাদের চেতনার দুয়ারে বার বার কড়া নেড়ে যাচ্ছেন একজন।
আমাদের সংগ্রামে, আমাদের জাগরণে, আমাদের অনুভবে এবং আমাদের চলার পথে তিনি আছেন সাহসের মশালহাতে নিয়ে!
আমাদের সকল সংগ্রাম ও আন্দোলনের প্রেরণার উৎস হিসেবে জেগে আছেন হাজী শরীয়তুল্লাহ!
তাঁর মতো ক্ষণজন্মা পুরুষেরা কখনো মরেন না।
তাদের কোনো মৃত্যু নেই।
যুগ যুগ ধরে বেঁচে থাকেনতাঁরা মানুষের চেতনায়।
মানুষের ভালোবাসায়। মানুষের শ্রদ্ধায়।
যেমন বেঁচে আছেন আমাদের সংগ্রামের উজ্জ্বল পুরুষ- হাজী শরীয়তুল্লাহ!
ফরায়েজী আন্দোলন নিয়ে
কৃষক কবিদের পুঁথি থেকে
“মহরমে এমামহাছেন হোছেনের।
হায় হায় জারি ছিল মশরেকগণের।
পাঁচ পীরের নামেতে মোকাম উঠাইয়া
উপবাস করিত সে সকলে মিলিয়া
...................
লাগাছ গাড়িত বাড়ীর চারিধার।
সেসব বেদাত এসে হইল মেছমার।
হাজি শরীয়তুল্লঅহ হেথা তশরিফ আনিয়া।
দীন জারি করিলেন বাঙ্গালা জুড়িয়া।
বংশ তালিকা
হাজী শরীয়তুল্লাহ (১)
মোহসেন উদ্দীন আহমদ (দুদু মিয়া) (২) (জন্ম: ১৮১৯, মৃত্যু ১৮৬২)
মাওঃ গিয়াস উদ্দীন হায়দার
আঃ গাফফার (নয়া মিয়া) মৃত্যু-১৮৮৪
সাঈদ উদ্দীন আহমদ (৩) মৃত্যু-১৯০৬
আবা খালেদ রশীদ উদ্দীন আহমদ (৪) (পীর বাদশাহ মিয়া) মৃত্যু-১৯৬০
আবু ওয়অছে রাজিউদ্দীন আহমদ (নওয়াব মিয়া)
আবুল হাফজ মোহসেন উদ্দীন আহমদ (দুদু মিয়া) (৫)
আবু ইয়াহ্ইয়অ মহিউদ্দীন আহ দ (দাদা মিয়া)
আবুল কালাম মঈনুদ্দীন আহমদ (জোবায়ের)
খলিল উল্লাহ (হুমায়ুন)
সালাহউদ্দীন ্াহমদ
আদনান আহমদ
তুরহান আহমদ
সোহেলকাদার
ইউসুসুফ কাদার
পাপ্পু
আবুল হাসানাত মোহসলেহ উদ্দীন আহমাদ (আবা বকর)
মোয়াজ্জে উদ্দীন আহমাদ (মাহমুদ)
আবু হাসান (শোয়াইব)
হাসিব উদ্দীন আহমদ
শরফুদ্দীন আহমদ (জোনায়েদ)
রাজী উদ্দীন আহমাদ (আবা বকর) বেনে আমীন)
রশীদ উদ্দীন আহমাদ (ইয়াহইয়অ)
মহীব উদ্দীন আহমাদ (মুনাদ)
মবিন উদ্দীন আহমদ (নওশি)
হাজী শরীয়তুল্লাহ : বিলুপ্ত কবরের এপটাফ
রাজধানী কেন্দ্রস্থলে বংশালে জীর্ণ অবস্থায় পড়ে আছে ফরায়েজী আন্দোলনের দ্বিতীয় পুরুষ দুদু মিয়ার কবরটি।
সুচীপত্রঃ
আগের কথা
জন্ম ও শৈশব
কলকাতায় গমন
দুর্ঘটনার কবলে
মক্কা জীবনে
স্বদেশের দিকে
চারদিকে আঁধার কালো
আবারো মক্কার পথে
বারবার লড়ে যায় বীর
গর্জে উঠলেন সাহসী সৈনিক
ফরায়েজী আন্দোলন
একজন অভিভাবকের কথা
কৌশলী কর্মপন্থা
দারুল হরব
জুলুম নির্যাতন
পত্র-পত্রিকার ভাষ্য
সমাজ সংস্কারক
হান্টারের পরিচয়
হান্টারেরর অভিমত
কয়েকটি বিবেচনা
প্রতিপক্ষের শ্যৈন দৃষ্টি
একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য
ইতিহাসের পুনর্পাঠ
ইন্তিকাল
বংশ তালিকা
আগের কথা
জন্ম ও শৈশব
কলকাতায় গমন
দুর্ঘটনার কবলে
মক্কা জীবনে
স্বদেশের দিকে
চারদিকে আঁধার কালো
আবারো মক্কার পথে
বারবার লড়ে যায় বীর
গর্জে উঠলেন সাহসী সৈনিক
ফরায়েজী আন্দোলন
একজন অভিভাবকের কথা
কৌশলী কর্মপন্থা
দারুল হরব
জুলুম নির্যাতন
পত্র-পত্রিকার ভাষ্য
সমাজ সংস্কারক
হান্টারের পরিচয়
হান্টারেরর অভিমত
কয়েকটি বিবেচনা
প্রতিপক্ষের শ্যৈন দৃষ্টি
একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য
ইতিহাসের পুনর্পাঠ
ইন্তিকাল
বংশ তালিকা

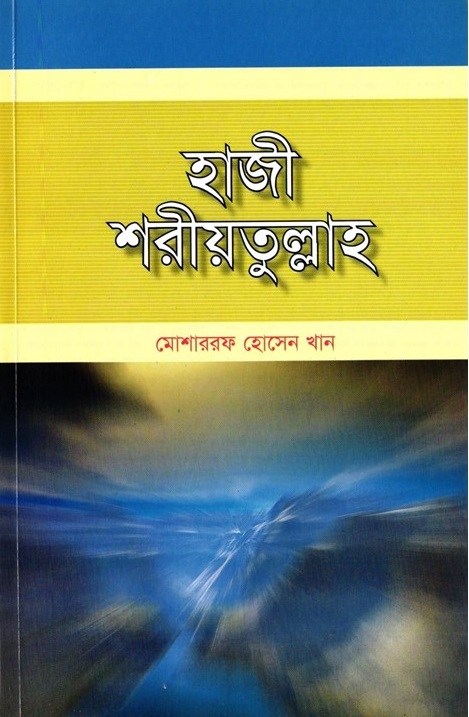 স্ক্যান কপি ডাউনলোড
স্ক্যান কপি ডাউনলোড