প্রকাশকের কথা
মুহতারাম আব্বাস আলী খান বাংলাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইসলামী চিন্তাবিদ। ইসলামের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার প্রয়াসে তাঁর অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইসলামী সাহিত্য রচনা ও অনুবাদের ক্ষেত্রেও তাঁর কলম ক্লান্তিহীন। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে ‘ইসলাম ও জাহেলিয়াতের চিরন্তন দ্বন্দ্ব’। এই গ্রন্থে লেখক সুনিপুণভাবে অতীত ও বর্তমানকালে ইসলামের সাথে জাহেলিয়াতের যে সংঘাত চলেছে ও চলছে তার চিত্র অঙ্কন করেছেন। সাথে সাথে তিনি ইসলাম প্রতিষ্ঠাকামীদের করণীয়ও নির্দেশ করেছেন সুন্দরভাবে। তাঁর গ্রন্থটি ইসলাম প্রতিষ্ঠাকামীদের মূল্যবান পাথেয় গণ্য হবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।
ইসলাম ও জাহেলিয়াত
ইসলাম ও জাহেলিয়াত দু’টি বিপরীতমুখী বিশ্বাস, মতবাদ ও কার্যক্রম। উভয়ের পথ, লক্ষ্য ও গন্তব্য ভিন্নতর – বরং বিপরীতমুখী। অতএব উভয়ের মধ্যে সংঘাত-সংঘর্ষ স্বাভাবিক ও অনিবার্য। মানবজাতির সূচনালগ্ন এ দ্বন্দ্ব-সংগ্রাম চলে আসছে এবং যতোদিন মানবজাতির অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকবে ততোদিন এ সংঘাত অব্যাহত থাকবে।
এ দু’টির একটি ভালো, অন্যটি মন্দ। একটি সত্য ও ন্যায়, অন্যটি মিথ্যা ও অন্যায়। একটি কল্যাণকর, অন্যটি অকল্যাণকর। একটি আলোক, অন্যটি অন্ধকার। একটি সৃজনশীল, অন্যটি ধ্বংসশীল। একটি বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহতায়ালার মনোনীত পথ, অন্যটি তাঁর অবাঞ্ছিত ও নিষিদ্ধ পথ। এ দু’টি পথ ও মতবাদের প্রথমটি ইসলাম, দ্বিতীয়টি জাহেলিয়াত। যা ইসলাম তা জাহেলিয়াত নয় এবং যা জাহেলিয়াত তা ইসলাম নয়।
‘জাহেলিয়াত’ শব্দটি ইসলামের বিপরীত অর্থে ব্যবহৃত হয়। ইসলামের যাবতীয় পন্থা-পদ্ধতি জ্ঞানভিত্তিক। কারণ, খোদা স্বয়ং সে পন্থাপদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন এবং তিনিই যাবতীয় গূঢ় রহস্যের জ্ঞান রাখেন। পক্ষান্তরে, ইসলাম থেকে ভিন্নতর প্রত্যেক পন্থা-পদ্ধতিই জাহেলিয়াতের পন্থা-পদ্ধতি বলে গণ্য। আরবের ইসলামপূর্ব যুগকে এ অর্থে জাহেলিয়াতের যুগ বলা হতো যে, সে যুগে জ্ঞান ছাড়াই নিছক কুসংস্কার, আন্দাজ-অনুমান এবং কামনা-বাসনার ভিত্তিতেই মানুষ তার নিজের জীবনপদ্ধতি নির্ধারিত করে নিয়েছিল। এ পদ্ধতি যেখানে যে যুগেই মানুষ অবলম্বন করবে, তাকে অবশ্যই জাহেলিয়াতের কর্মপদ্ধতি বলা হবে।
মোটকথা, ইসলামের পরিভাষায় জাহেলিয়াত বলতে সেসব কর্মপদ্ধতি বোঝায় যা ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতি, নীতি-নৈতিকতা, শিষ্টাচার ও মন-মানসিকতার পরিপন্থী। - ‘তিনিই সে মহান সত্তা যিনি তোমাদেরকে পয়দা করেছেন। অতঃপর তোমাদের মধ্যে কেউ কাফের, কেউ মুমিন এবং আল্লাহ সবকিছু লক্ষ্য করছেন, যা তোমরা করছ’- (তাগাবুনঃ ২)।
তাফসীরকারকগণ এর চারটি মর্ম বর্ণনা করেছেন এবং চারটিই সঠিক।
এক—তিনি তোমাদের স্রষ্টা। কিন্তু তাঁর স্রষ্টা হওয়াকে কেউ অস্বীকার করে এবং কেউ এ মহাসত্য মেনে নেয়। তাই তাদেরকে যথাক্রমে কাফের ও মুমেন বলা হয়েছে।
দুই—তিনি তোমাদেরকে পয়দা করে ভালো ও মন্দ উভয় পথ দেখিয়ে দিয়েছেন এবং উভয়ের পরিণাম ফলও বলে দিয়েছেন। অতঃপর এ দু’টি পথের যে কোন একটি বেছে নেয়ার এবং সে পথে চলার পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছেন। তোমরা কুফর অবলম্বন করতে চাইলে অর্থাৎ আল্লাহর পথে চলতে অস্বীকার করতে চাইলে তা করতে পার এবং ঈমান এনে তাঁর পথে চলতে চাইলে তাও করতে পার। ঈমান ও কুফরের কোন একটি অবলম্বন করতে তিনি তোমাদেরকে বাধ্য করেন না। অতএব ঈমান ও কুফর অর্থাৎ আল্লাহর প্রভুত্ব-কর্তৃত্ব ও হুকুম-শাসন মেনে নেয়া কিংবা না নেয়া – এ উভয়ের জন্যে তোমরা স্বয়ং দায়ী। এ দু’টির যে কোন একটি গ্রহণের এখতিয়ার-স্বাধীনতা তোমাদেরকে দিয়ে তিনি তোমাদেরকে ভয়ানক পরীক্ষায় ফেলেছেন। তিনি লক্ষ্য রাখছেন যে, তোমরা তোমাদের এখতিয়ার কিভাবে ব্যবহার করছ। ‘তিনি লক্ষ্য করছেন যা তোমরা করছ’ – কথাটির মধ্যে সতর্ক করে দেয়ার ইঙ্গিত রয়েছে। দু’টি বিপরীত পথে চলার যেমন স্বাধীনতা আছে, তেমনি দুই বিপরীতমুখী পরিণামফলও অবশ্যই ভোগ করতে হবে। ভালো ও মন্দ পথের পরিণাম কখনো একই রকম হতে পারে না। ভাল পরিনাম ভোগ করতে হলে ভালো পথেই চলতে হবে, এ কথা বলার কোন প্রয়োজন করে না। এখানেই মানুষের পরীক্ষা। পুরস্কার ও শাস্তির জন্যেই পরীক্ষা করা হয়। নতুবা পরীক্ষা অর্থহীন হয়ে পড়ে।
তিন—তিনি তোমাদেরকে সুস্থ-সঠিক স্বভাব-প্রকৃতির উপর পয়দা করেছেন এবং তার দাবিই এই যে, তোমরা ঈমানের পথ অবলম্বন করবে। কিন্তু সুস্থ-সঠিক স্বভাব-প্রকৃতির উপর পয়দা হওয়ার পর তোমাদের মধ্যে কেউ কুফর অবলম্বন করেছ যা তাঁর সৃষ্টির পরিপন্থী। আবার কেউ ঈমানের পথ অবলম্বন করেছ, যা তার স্বভাব-প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যশীল।
মনে রাখতে হবে, মানুষকে পাপ-প্রবণতাহীন প্রকৃতিগত মন-মানসসহ পয়দা করা হয়েছে। অতঃপর সে সৎপথ অথবা অসৎপথ অবলম্বন করে।
উল্লেখ্য যে, দুনিয়ায় যতো নবী-রাসূল এসেছেন এবং তাঁদের যেসব আসমানী কিতাব দেয়া হয়েছে, তার কোনটিতেই মানুষকে জন্মগত পাপী বলে উল্লেখ করা হয়নি। অথচ দেড় শতাব্দী যাবত খৃস্টীয় জগত এ ধর্মীয় বিশ্বাস পোষণ করে আসছে যে, মানুষ জন্মগতভাবে পাপী। তাদে বিশ্বাস, হযরত আদম(আঃ) ও হাওয়ার পাপের পরিণাম হিসেবে মানুষের মধ্যে বংশানুক্রমিক পাপপ্রবণতা চলে আসছে। তার তাদের পাপপ্রবণতা দমিত করার চিন্তা ও চেষ্টা-চরিত না করে তার সকল দায়দায়িত্ব হযরত আদম(আঃ) ও বিবি হাওয়ার উপর চাপিয়ে দিয়ে পাপপংকিল জীবন-যাপন করার বাহান তালাশ করে নিয়েছে। এ এক মারাত্মক ভ্রান্ত চিন্তাধারা ও দর্শন এবং এটাই জাহেলিয়াত।
তবে বর্তমানে ক্যাথলিক পণ্ডিতগণ বলা শুরু করেছেন যে, বাইবেলে এ ধারণা, বিশ্বাসের কোন ভিত্তি নেই। বাইবেল গ্রন্থের প্রখ্যাত পণ্ডিত রেভারেন্ড হাবাট হাগ তার ‘Is Original Sin in Scripture?’গ্রন্থে বলেন, তৃতীয় শতক পর্যন্ত খৃস্টানদের মধ্যে এ ধরনের বিশ্বাস ছিল না যে, মানুষ জন্মগতভাবে পাপী। কিছু লোকের প্রচারণায় এ ধরনের ধারণা-বিশ্বাস যখন ছড়িয়ে পড়তে থাকে, তখন দুই শতাব্দী পর্যন্ত খৃস্টান পণ্ডিতগণ এর প্রতিবাদ করতে থাকেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পঞ্চম শতকে সেইন্ট অগাস্টাইন তার কূটযুক্তি জালের বলে এ কথাটি খৃস্টান ধর্মের মৌলিক বিশ্বাসের মধ্যে শামিল করে দেন যে, মানবজাতি আদমের পাপের অভিশাপ উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেছে। আর যিশুখৃস্টের শূলীতে জীবন দান করে কাফফারা দেয়ার ফলে মানুষের মুক্তিলাভের ব্যবস্থা করা হয়েছে – তাছাড়া আর কোন উপায় নেই। এ এক ভ্রান্ত, মনগড়া ও অযৌক্তিক অন্ধবিশ্বাস এবং জাহেলিয়াতের এ এক মারাত্মক অস্ত্র।
চার- আল্লাহ তায়ালাই তোমাদেরকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব দান করেছেন। তোমরা ছিলে না, পরে হয়েছো। এ বিষয়টি সম্পর্কে তোমরা যদি সহজ-সরল ও নিরপেক্ষ মন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে তাহলে অবশ্যই বুঝতে পারতে যে, তোমাদের অস্তিত্বই খোদার এক বিশেষ দান যার ফলে তোমরা তোমাদের জন্যে সৃষ্ট অসংখ্য-অগণিত নিয়ামত ভোগ করতে পারছ। কিন্তু তোমাদের মধ্যে অনেকেই এ বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করে না। এর ফলে তারা বিদ্রোহ ও পাপাচারের পথ অবলম্বন করেছে। আর কতিপয় লোক ঈমানের পথ অবলম্বন করে সঠিক ও নির্ভুল চিন্তার পরিচয় দিয়েছে।
কুরআন পাকের সূরায়ে রূমে যা কিছু বলা হয়েছে তাও বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। ‘অতএব (হে নবী ও নবীর অনুসারীগণ) একমুখী হয়ে নিজেদের সকল লক্ষ্য এ দ্বীনের প্রতি কেন্দ্রীভূত করে দাও। দাঁড়িয়ে যাও সেই প্রকৃতির উপর যার উপর মানুষকে আল্লাহ পয়দা করেছেন। আল্লাহর বানানো কাঠামো বদলানো যায় না। এই হচ্ছে একেবারে সত্য-সঠিক দ্বীন বা জীবন ব্যবস্থা’- (রূমঃ ৩০)।
উপরোক্ত আয়াতে নবী মুহাম্মাদ (সা) এবং মুসলমানদেরকে সম্বোধন করে বলা হচ্ছে- এ বাস্তবতা তোমাদের কাছে যখন সুস্পষ্ট যে, এ বিশ্বজগতের স্রষ্টা ও মালিক একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কেউ নেই, তখন অনিবার্যরূপে তোমাদের কর্মপন্থা যা হওয়া দরকার তা হচ্ছে এই যে, তোমাদের লক্ষ্য একনিষ্ঠভাবে এ দ্বীনের প্রতি কেন্দ্রীভূত কর। এ দ্বীন হচ্ছে তা-ই যা কুরআন পেশ করছে। এ দ্বীন অনুযায়ী ইবাদত বন্দেগী, দাসত্ব, আনুগত্য লাভের অধিকারী এক ও লাশরীক আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ নেই। এ দ্বীন থেকে মুখ ফিরিয়ে অন্য কোন দিকে মুখ করো না। জীবনের জন্যে এ পথ অবলম্বন করার পর অন্য কোন পথের দিকে যেন না তাকাও। সমগ্র মানবজাতিকে এ স্বভাব-প্রকৃতির উপর পয়দা করা হয়েছে যে, এক আল্লাহ ব্যতীত তাদের কোন স্রষ্টা, কোন প্রভু, কোন মাবুদ এবং এমন কোন সত্তা নেই সত্যিকার অর্থে যার আনুগত্য করা যেতে পারে। এ স্বভাব-প্রকৃতির উপরই মানুষকে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে।
‘আল্লাহর বানানো কাঠামো বদলানো যায় না’- বাক্যের অর্থ এই যে, খোদা মানুষকে তাঁর বান্দারূপে পয়দা করেছেন। যেন মানুষ একমাত্র তাঁরই বন্দেগী করে। সৃষ্টির এ স্বাভাবিক ধারা-প্রকৃতি কারো পক্ষে বদলানো সম্ভব নয়। এ অবস্থা থেকে ‘খোদার দাস নয়’ অবস্থায় পরিবর্তিত হওয়া সম্ভব নয়। খোদা নয় এমন কাউকে খোদা গণ্য করলে সত্যিকার অর্থে সে খোদা হয়ে যেতে পারে না। মানুষ নিজের জন্যে যত খুশি উপাস্য বানিয়ে নিক না কেন, এক খোদা ছাড়া মানুষ আর কারো বান্দাহ নয়, হতে পারে না।
এ আলোচনার সারমর্ম এই যে, আল্লাহতায়ালা একদিকে মানুষকে স্বাধীনভাবে তার নিজের জীবনপথ বেছে নেয়ার এবং তদনুযায়ী কাজ করার পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছেন। অপরদিকে প্রকৃত সত্যকে তার কাছে সুস্পষ্ট করে তুলে ধরছেন এবং এ সত্যকে গ্রহণ করার আহ্বান জানাচ্ছেন।
আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন বলে তাকে খুব ভালোবাসেন। তার জীবনের সকল প্রয়োজন পূরণের জন্যে অসংখ্য-অগণিত বস্তু ও দ্রব্যসম্ভার তার চারদিকের পৃথিবীতে ছড়িয়ে রেখেছেন। চন্দ্র-সূর্য-তারকারাজি, দিবারাত্রি। আলো-বাতাস, আকাশের মেঘমালা ও বারিবর্ষণ, পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী, গাছপালা, পশুপাখি এবং নানাবিধ আহার্য দ্রব্য- মানুষের জন্যেই তিনি সৃষ্টি করেছেন। তিনি যে মানুষকে ভালোবাসেন এসব তারই নিদর্শন। আর মানুষকে ভালোবাসেন বলেই তিনি মানুষকে তার জীবনের সঠিক পথটি অবশ্যই বলে দেবেন। এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক। মানুষের দুনিয়ার স্বল্পকালীন জীবন কিভাবে সুখী ও সুন্দর হতে পারে এবং দুনিয়ার জীবনের পর পরকালীন চিরন্তন জীবনও কিভাবে সার্থক হতে পারে, তার বিধিবিধান, নিয়মকানুন ও কর্মসূচি তাকে বলে দেবেন না, এমনটি চিন্তা করা যায় না। প্রকৃতপক্ষে তিনি তা বলেও দিয়েছেন। নবী-রসূলগণের মাধ্যমে তিনি মানুষকে তার পূর্ণ জীবনবিধান বলে দিয়েছেন। এটাকেই বলা হয়েছে স্বভাব-প্রকৃতিসুলভ দ্বীন যার উল্লেখ উপরে করা হলো।
মানুষকে জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেক দান করে তাকে পরীক্ষা করার জন্যে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেয়া হয়েছে, তার জীবনের জন্যে যে কোন পথ বেছে নেয়ার এবং তদনুযায়ী স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ দেয়। সে ইচ্ছা করলে খোদার বলে দেয়া পথে চলে তার সুফল লাভ করতে পারে অথবা এ পথ পরিত্যাগ করে তার মনগড়া কোন ভ্রান্ত পথেও চলতে পারে। সে আল্লাহকে তার একমাত্র স্রষ্টা, প্রতিপালক, প্রভু ও শাসক মনে করে তাঁর পরিপূর্ণ আনুগত্য করতে পারে, অথবা সে কল্পিত বহু ভ্রান্ত খোদার উপাসনাও করতে পারে। এ দু’টি পথের যে কোন একটি পথ অবলম্বন করার স্বাধীনতা থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ যুগে যুগে প্রত্যেক জাতি ও কওমের কাছে নবী-রসূল পাঠিয়ে মানুষকে তার জীবনের সঠিক পথ সম্পর্কে বার বার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। সঠিক পথে চলতে যে স্বাধীনতা তাকে দেয়া হয়েছে তা খর্ব করতে চাননি, বরং সঠিক পথে চলার মঙ্গলকারিতা বর্ণনা করে তাকে সম্মত করার ও উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করা হয়েছে। অপরদিকে ভ্রান্ত পথে চলার ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে অবহিত করে সে পথে চলা থেকে বিরত রাখার চেষ্টাও করা হয়েছে।
মানব ইতিহাসের এমন কোন যুগ বা সময়কাল অতীত হয়নি যখন মানুষকে খোদার পথে আহ্বান জানানোর জন্যে কোন নবী অথবা তাঁর স্থলাভিষিক্ত বিদ্যমান থাকেননি। এই যে পরম্পরা ও খোদার পথে মানুষকে আহবানের অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতা এরও বিশেষ প্রয়োজন ছিল এবং এখনও রয়েছে। তার কারণ এই যে- খোদার পথ পরিহার করে অন্য যে কোন পথ অবলম্বন করলে- তা হয় প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রামেরই নামান্তর। এর ফলে মানুষের জীবনে নেমে আসে নানান বিপর্যয় ও দুর্যোগ। মানুষের উপর মানুষের প্রভুত্ব কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। সবল দুর্বলের খোদা হয়ে বসে। অসংখ্য-অগণিত মানুষ মানুষের গোলামির শৃংখলে আবদ্ধ হয়। নিষ্ঠুর ও অত্যাচারী শাসকের নির্যাতন-নিষ্পেষণে মানুষের আর্তনাদ-হাহাকারে আকাশ-বাতাস ভরে যায়। মানুষের এসব নির্যাতন নিষ্পেষণের অবসান ঘটিয়ে তাদের স্বাধীনতা, সুখশান্তি ও জানমালের নিরাপত্তা বিধানের জন্যে খোদার পথে মানুষকে আহ্বান জানাবার প্রয়োজন যেম্মন অতীতে ছিল, এখনো আছে এবং ভবিষ্যতেও হবে। এটাই আল্লাহ তায়ালার অটল নীতি। এ নীতি মেনে চলার নামই ইসলাম এবং এর বিপরীত যতোকিছু তার সমষ্টিকেই বলে জাহেলিয়াত। যা সত্য তা ইসলাম এবং মিথ্যা ও ভ্রান্তই জাহেলিয়াত।
সত্য ও মিথ্যা পরস্পর বিরোধী শক্তি
উপরের আলোচনায় এ কথা পরিষ্কার হয়েছে যে, ঈমান ও কুফর যেমন বিপরীতমুখী, ইসলাম ও জাহেলিয়াতও তেমনি বিপরীতমুখী। ইসলাম আল্লাহ তায়ালার বলে দেয়া পথ ও পন্থা এবং জীবনের এক কল্যাণমুখী কর্মসূচি। খোদাপ্রদত্ত অভ্রান্ত জ্ঞানই এর উৎসকেন্দ্র। মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেকও তা-ই সমর্থন করে এবং স্বভাব-প্রকৃতির সাথেও এ সংগতিশীল। অপরদিকে কুফর তথা অজ্ঞানতার অন্ধকার, আন্দাজ-অনুমান ও অলীক কল্পনা থেকে জাহেলিয়াত উৎসারিত। অতএব প্রথমটি সত্য ও সুন্দর, দ্বিতীয়টি মিথ্যা ও কুৎসিত। প্রথমটি আলোক, দ্বিতীয়টি অন্ধকার। এ দু’টির একটি অপরটিকে কখনোই বরদাশত করতে পারে না। তাই একটি অপরটির প্রতিদ্বন্দ্বী শিক্তি। তাদের পারস্পরিক সংঘাত-সংঘর্ষও চিরন্তন।
জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেক
আল্লাহ তায়ালা মানুষকে যে জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেক দান করেছেন তার বদৌলতেই সে জীবশ্রেষ্ঠ হিসেবে পরিচিত। এ বিশেষ গুণটি মানুষ ও অন্যান্য জীবের মধ্যে বিরাট পার্থক্য সূচিত করেছে। মানুষ তার প্রতিটি কাজের জন্যে যে স্বয়ং দায়ী, জ্ঞান-বুদ্ধি তার মধ্যে এ অনুভূতি সৃষ্টি করে। পক্ষান্তরে, যাকে জ্ঞান-বুদ্ধি দান করা হয়নি, তার বেলায় এ নীতি প্রযোজ্য নয়। যেমন ধরুন, উপর থেকে যদি একটি ভারি পাথর হঠাৎ স্থানচ্যুত হয়ে পতিত হয়ে কোন ব্যক্তিকে মেরে ফেলে, তাহলে পাথরটিকে কিছুতেই অপরাধী গণ্য করা যাবে না। কারণ সে একটা নিষ্প্রাণ অচেতন পদার্থ মাত্র। ঠিক এভাবে কোন একটি পশু কারো শস্যক্ষেতে প্রবেশ করে ফসল খেয়ে তছনছ করলো, তাহলে তাকেও অপরাধী বলা যাবে না। কারণ তার মধ্যে চেতনা ও অনুভূতি থাকলেও সে জ্ঞানবুদ্ধি বিবর্জিত। কিন্তু এ ধরনের কোন কাজ যদি মানুষ করে বসে, তাহলে তাকে অবশ্যই দোষী বলে গণ্য করা হবে এবং আইনের বিচারে তাকে শাস্তি পেতে হবে। কারণ তাকে চেতনা ও অনুভূতির সাথে জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেকের গুণে গুণান্বিত করা হয়েছে। এর দ্বারা সে ন্যায় ও অন্যায় উপলব্ধি করতে পারে। নিষ্প্রাণ ও অজৈব অচেতন পদার্থ এবং মানুষ ব্যতীত অন্যান্য প্রাণী উপরোক্ত গুণ ও ভালো-মন্দ নির্ণয়ের যোগ্যতা থেকে বঞ্চিত বিধায় তাদের কোন কাজের জন্যে জবাবদিহি করতে হয় না। মানুষ তার কাজের জন্যে স্বয়ং দায়ী তার কারণ এই যে, তাকে জ্ঞান-বুদ্ধি দ্বারা ভূষিত করা হয়েছে।
জ্ঞান-বুদ্ধির সদব্যবহার
মানুষকে জ্ঞান-বুদ্ধি দান করে মহানতম মর্যাদা দেয়া হলেও সে জ্ঞানের অপব্যবহার করে। তাকে বুদ্ধি-বিবেক দান করে ভালো-মন্দ ও ন্যায়-অন্যায় জেনে নেয়ার যোগ্যতাসম্পন্ন করার পরও তার প্রতিটি কাজ যে বিবেকসম্পন্ন হবে তেমন কথা বলা যায় না। এর দৃষ্টান্তের অভাব নেই। বরং আমাদের চারধারে এর অসংখ্য দৃষ্টান্ত দেখতে পাই। যেমন ছাত্রদের কথাই ধরুন। অভিভাবকগণ তাদের সন্তানকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠান জ্ঞান ও মানবীয় গুণাবলী অর্জনের জন্যে। তার জন্যে তাঁরা তাদের শিক্ষার যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করেন। বিবেকের দাবিই এই ছিল যে, প্রতিটি ছাত্র নিয়মিত পড়াশোনা করবে, তার যোগ্যতা ও মেধা অনুযায়ী যথাসম্ভব পরীক্ষায় ভাল ফল লাভ করে ভালো ছাত্র হওয়ার প্রশংসা অর্জন করবে। এ জ্ঞান, বিশ্বাস ও অনুভূতি প্রতিটি ছাত্রের মধ্যে বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও আমরা কি দেখি? কতিপয় ছাত্র তাদের দায়িত্ব পুরোপুরি পালন করার চেষ্টা করে। আবার অনেকে তাদের দায়িত্ব-কর্তব্য অবহেলা করে এমন সব গর্হিত কর্মকাণ্ডে সময় ক্ষেপণ করে যা কোন দিক দিয়েই বাঞ্ছিত নয়। মানুষ হিসেবে এ উভয় প্রকারের ছাত্র জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেকের অধিকারী। কিন্তু উভয় ধরনের ছাত্রকে একইভাবে তাদের বুদ্ধি ও বিবেককে কাজে লাগাতে দেখা যায় না। এর থেকে জানতে পারা যায় যে, সকলে তাদের বিবেকের সদ্ব্যবহার করতে পারে না।
আবার ক্ষমতাপিপাসু একদল লোক ক্ষমতা লাভের জন্যে- যে কোন হীনপন্থা অবলম্বন করতে দ্বিধাবোধ করে না। তাদের মধ্যে অনেকেই উচ্চশিক্ষিত ও উচ্চডিগ্রিধারীও থাকে। কিন্তু দুর্নীতি, বলপ্রয়োগ, হত্যাকাণ্ড, সন্ত্রাস প্রভৃতির মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করে তারা মানুষের প্রভু হয়ে বসে। অতঃপর মানুষের মৌলিক অধিকার পূরণ করার পরিবর্তে তাদেরকে গোলামির শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে মানবেতর জীবন যাপন করতে বাধ্য করে। এ চিত্র দুনিয়ায় বহুস্থানে অতীতেও দেখা গেছে, এখনও দেখা যাচ্ছে। লুটতরাজ, হত্যা, রাষ্ট্রীয় সম্পদ আত্মসাৎ, চুরি-ডাকাতি প্রভৃতি ঘটনা তো সমাজে অহরহ ঘটছে। এসব যাদের দ্বারা সংঘটিত হচ্ছে তারা সকলেই মানুষ এবং শিক্ষিত বলে পরিচিত। জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেক তাদেরও অবশ্যই থাকার কথা। কিন্তু তার সদ্ব্যবহার তারা করছে কোথায়?
দুনিয়ায় এখনও এমন কতগুলো দেশ আছে যাদেরকে অনুন্নত বলা হয়। শিক্ষা-দীক্ষায় অনগ্রসর, দারিদ্র্য পীড়িত। এসব দেশে অমন ধরনের অবস্থাকে কেউ কেউ ততোটা দূষণীয় মনে করেন না। তাদের সাথে একমত হওয়ার কোন কারণ না থাকলেও সর্বদিক দিয়ে উন্নত ও সুসভ্য দেশ বলে পরিচিত দেশগুলোতে কি ঘটছে? বর্তমানে ইংল্যান্ড ও যুক্তরাষ্ট্রকে উন্নতি ও সভ্যতার উচ্চশিখরে আরোহণকারী দেশ বলে বিবেচনা করা হয়। জ্ঞান ও সভ্যতার দীক্ষা গ্রহণের জন্যে এ দু’টি দেশে মানুষের ভিড় লেগেই থাকে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যায় এ দু’টি দেশ শীর্ষস্থান অধিকার করে থাকলেও জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেকের সদ্ব্যবহারে সম্পূর্ণ ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। অপর জাতির উপর অত্যাচার অবিচারে তারা সিদ্ধহস্ত। আপন সমাজেও তারা নৈতিক অধঃপতনের অতল তলে নিমজ্জিত। ১৯৮৮ সালের ২৭শে জুনের ‘নিউজ উইকে’ প্রকাশিত একটি খবর থেকে তাদের চরম নৈতিক অবক্ষয় ও ক্রমবর্ধমান অপরাধপ্রীতি জানতে পারা যায়। খবরে বলা হয়েছে, সাত মিলিয়ন লোকের শহর লন্ডনে গতবছর (১৯৮৭) ১৯৪টি হত্যাকাণ্ড এবং ২২,৬২৬টি ভয়ানক হিংসাত্মক অপরাধ সংঘটিত হয়েছে। ওদিকে নিউইয়র্ক শহরে ১৬৭২টি হত্যাকাণ্ড এবং ১,৪৮,৩১৩টি হিংসাত্মক অপরাধ সংঘটিত হয়েছে। এ শুধু দু’দেশের দু’টি শহরের অবস্থা। এসব অপরাধীদের জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেক কোথায় গেল?
জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেক থাকাটাই যথেষ্ট নয়; তার সদ্ব্যবহারই প্রকৃত মানুষের কাজ। উপরের দৃষ্টান্তগুলো থেকে বুঝতে পারা গেল যে, সকলে তাদের জ্ঞান-বিবেকের সদ্ব্যবহার করতে পারে না। কেউ সদ্ব্যবহার করতে সমর্থ হলেও কেউ আবার ব্যর্থতার পরিচয় দেয়।
এ ব্যর্থতার কারণ কি?
এতো বড়ো মারাত্মক ভুল মানুষ করে কেন? তার মহামূল্য সম্পদ জ্ঞান-বুদ্ধির প্রতি সে এতো বড়ো জুলুম করে কেন? সামনে অগ্রসর হওয়ার পূর্বে এর জবাব আমাদের অবশ্যই পেতে হবে।
প্রথম কথা এই যে, মানুষের স্বভাবজাত দু’টি বিপরীতমুখী প্রবণতা রয়েছে। একটি খোদাভীরুতা বা সুকৃতির প্রবণতা এবং অপরটি দুষ্কৃতির প্রবণতা। এ দু’টির মধ্যে সংঘাত-সংঘর্ষ সর্বদা বিদ্যমান। উভয়টি তাদের দাবি পূরণের জন্যে মানুষকে উদ্বুদ্ধ, উত্তেজিত ও প্ররোচিত করে। সুকৃতির প্রবণতা বিজয়ী হলে মানুষ তার জ্ঞান-বুদ্ধির সদ্ব্যবহার করে সৎ কার্য সম্পাদন করে। আবার দুষ্কৃতি-প্রবণতা বিজয়ী হলে সে মানুষকে নানান পাপাচারে লিপ্ত করে।
দুষ্কৃতির প্রবণতা বিজয়ী হয় কয়েকটি কারণে। তার মৌলিক কারণগুলো নিম্নরূপ।
প্রথমটি হলো- মানুষের প্রবল কুপ্রবৃত্তি ও তার কামনা-বাসনা। এ কামনা-বাসনা এতোটা শক্তিশালী যে মানুষ সাধারণতঃ তার কাছে অসহায় হয়ে পড়ে। তা দমন করার শক্তি হারিয়ে ফেললে মানুষ প্রবৃত্তির দাস হয়ে পড়ে। তখন যে কোন অন্যায়, অনাচার, পাপাচার ও পশুসুলভ কাজ করতে সে মোটেও দ্বিধাবোধ করে না। সে তার প্রবৃত্তিকেই তার ‘ইলাহ’ বানিয়ে নেয় এবং নিজে পুরোপুরি প্রবৃত্তির দাস হয়ে পড়ে। প্রবৃত্তির দাস হওয়ার পর ভালোমন্দের জ্ঞান তার লোপ পায়। অনেক সময় পাপকে পাপ বলে বিশ্বাস করার পরও তা থেকে দূরে থাকার শক্তি তার থাকে না। যেমন চুরি, ডাকাতি, খুন খারাবি, ব্যভিচার প্রভৃতি খারাপ মনে করা সত্ত্বেও মানুষ প্রবৃত্তির দাসত্ব করতে গিয়ে এসব পাপাচার থেকে বাঁচতে পারে না।
কুপ্রবৃত্তি সামনে অগ্রসর হয়ে মানুষকে দুনিয়াপূজারী বানিয়ে ফেলে। দুনিয়ায় ভোগ-বিলাস তখন তার জীবনের লক্ষ্য হয়ে পড়ে। কথায় বলে, তিনটি বস্তুর প্রতি মানুষের আসক্তি সর্বাধিক- অর্থ, নারী ও মাদকদ্রব্য। এ তিনটির জন্যে দুনিয়ায় যে কতশত লংকাকাণ্ড ঘটেছে, তার দৃষ্টান্তে ইতিহাস ভরপুর। দুনিয়ায় কে কত বড়ো ও শক্তিশালী হতে পারে, কে কত ধন-ঐশ্বর্যের পাহাড় গড়তে পারে, কে কত মানুষকে তার দাস বানাতে পারে, কে কত নারীর যৌবন সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারে, প্রবৃত্তির দাসেরা তারই এক প্রতিযোগিতায় মেতে যায়। খোদা ও আখেরাতের ভয় যেন ক্ষণিকের জন্যে তাদের চিত্ত বিচলিত করতে না পারে, তার জন্যে মনগড়া দর্শন ও মতবাদ সৃষ্টি করা হয়েছে। খোদা বা সৃষ্টিকর্তা বলে কোন শক্তির অস্তিত্ব নেই। আখেরাত এক অবাস্তব ও গাজাঁখুরি চিন্তার ফসল। এ দুনিয়া এবং দুনিয়ার জীবনটাই সবকিছু। জীবনটা একটা বেঁচে থাকার ও টিকে থাকার সংগ্রাম- STRUGGLE FOR EXISTENCE.
এখানে যে শক্তিমান তারই টিকে থাকার, কর্তৃত্ব প্রভুত্ব করার, জীবনকে ষোলআনা উপভোগ করার অধিকার আছে। দুর্বলের বেঁচে থাকার অধিকার নেই- SURVIVAL OF THE FITTEST.
এ দর্শনে বিশ্বাসী হওয়ার পর ন্যায়-অন্যায়, বৈধ-অবৈধ, ভালো-মন্দ, দয়া-নিষ্ঠুরতার কোন প্রশ্ন মনে জাগ্রত হওয়ার কথা নয়। লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্যে যা কিছু প্রয়োজন তা-ই করা হয়। মিথ্যা, প্রতারণা, বিশ্বাসঘাতকতা, ওয়াদাভংগ, হত্যা, লুণ্ঠন, সন্ত্রাস, বলপ্রয়োগ, মিথ্যা-বানোয়াট অপবাদ প্রভৃতির সুযোগ গ্রহণ করা হয়। এসব কোন কাল্পনিক কথা নয়। এসব অতীত ও বর্তমান ইতিহাসের বাস্তব ঘটনা। জাহেলিয়াতের এ এক ভয়ংকর রূপ।
দ্বিতীয় মৌলিক কারণ হলো- জাতীয়, দলীয় ও বংশীয় গর্ব-অহংকার ও তার প্রতি অন্ধপ্রীতি। বাপদাদা ও ধর্মীয় নেতাদের, বংশানুক্রমিক চিন্তাধারা ও রীতিনীতির এবং নানাবিধ কুসংস্কারের অন্ধ অনুসরণ। এ অন্ধপ্রীতি ও অন্ধ অনুসরণ মানুষকে ভালো-মন্দ ও ন্যায়-অন্যায়ের বিচারবোধ থেকে বঞ্চিত করে। আপন জাতি, দল ও বংশের জন্যে যা ভালো ও লাভজনক- তা অন্যের জন্যে যতোই ক্ষতিকর হোক না কেন, তা-ই করার জন্যে মানুষ সর্বশক্তি প্রয়োগ করে, যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হয়। ইংল্যান্ডের ইতিহাসে সাত বছর, তিরিশ বছর ও একশ’ বছর ব্যাপী যুদ্ধের উল্লেখ আছে। এ জাতীয় ও বংশীয় গর্ব-অহংকার ও অন্ধপ্রীতিরই কুফল। প্রাক-ইসলামী যুগে আরব ভূখণ্ডেও এ ধরনের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ চলেছে বংশানুক্রমে। প্রবৃত্তির কামনা বাসনা পূরণ করতে গিয়ে মানুষের খুনের দরিয়া প্রবাহিত করা হয়েছে।
গায়ের জোরে অপরের ভূখণ্ড দখল এবং দুর্বল জাতিকে পদানত করার অদম্য লালসা দু’টি বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত করে। জাহেলিয়াতের দানবদের দ্বারা প্রথম বিশ্বযুদ্ধ তার প্রচণ্ড ও হিংস্র থাবা বিস্তার করে আটাশটি দেশ ও ছ’টি মহাদেশের উপর। এ যুদ্ধে এক কোটি সৈন্য ও এক কোটি বেসামরিক লোক প্রাণ হারায়। যুদ্ধজনিত দুর্ভিক্ষ, মহামারী ও রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে আরও দু’কোটি মানুষ ধরাপৃষ্ঠ থেকে চিরতরে বিদায় হয়।
একুশ বছর পর জাহেলিয়াতের দানবদের ক্ষমতার অতৃপ্ত লালসা চরিতার্থ করার জন্যে অধিক হিংস্রতা, হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ নিয়ে আসে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। এ মহাযুদ্ধ পৃথিবীর প্রতিটি দেশ ও জাতিকেই যুদ্ধে কোন না কোন প্রকারে জড়িত করে ফেলে। সতেরো মিলিয়ন সৈন্য ও একচল্লিশ মিলিয়ন বেসামরিক লোক মৃত্যুর করালগ্রাসে ঢলে পড়ে। যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবহৃত অমানবিক আণবিক বোমায় জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকির লক্ষ লক্ষ মানুষ নিহত হয়, লক্ষ লক্ষ মানুষ পঙ্গু ও বিকলাংগ হয়। লক্ষ লক্ষ মানুষ ধুঁকে ধুঁকে মৃত্যুবরণ করে। এর চেয়ে অধিক বর্বরতা ও পাশবিকতা অতীত জাহেলিয়াতের যুগে কখনো অনুষ্ঠিত হয়নি। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি আধুনিক জাহেলিয়াতকে অতীত জাহেলিয়াত থেকে হিংস্রতর করেছে।
বংশানুক্রমিক ধারণা-বিশ্বাস, রীতিনীতি ও রসম-রেওয়াজ এবং ধর্মীয় নেতাদের অন্ধ অনুসৃতি এক মারাত্মক মানসিক ব্যাধি, যার পেছনে প্রবৃত্তির প্রবল প্ররোচনা কাজ করে। ইসলামের ইতিহাস এ কথার সাক্ষ্য দান করে যে, নবী-রসূলগণ যখন মানুষের কাছে ইসলামের দাওয়াত পেশ করেছেন তখন তারা এই বলে প্রত্যাখ্যান করেছে যে, বংশানুক্রমে তারা এবং তাদের বাপ-দাদারা যে ধর্মীয় বিশ্বাস পোষণ করছে, যে রেওয়াজ ও রীতিনীতি আবহমান কাল থেকে তারা পালন করে আসছে, তাদের ধর্মীয় নেতারা যা কিছু বলছে, নবী তার বিপরীত কথা বলছেন। অতএব তা কিছুতেই মেনে নেয়া যেতে পারে না। এসব আলোচনা যথাস্থানে করা হবে।
ধর্মীয় নেতা ও পীর-পুরোহিতের প্রতি সীমাহীন ভক্তি-শ্রদ্ধা তাদেরকে খোদার আসনে বসিয়ে দেয়। তাদেরকে নিষ্পাপ মনে করা হয় এবং তাদের মুখ থেকে যা কিছুই বেরোয় তার সত্যাসত্য বিচার না করেই তাকে বেদবাক্য অথবা খোদার ওহীর মতো অকাট্য সত্য বলে বিশ্বাস করা হয়। আল্লাহ স্বয়ং বলেন-
‘এসব লোক তাদের আলেম-পীর-দরবেশকে আল্লাহকে বাদ দিয়ে নিজেদের খোদা বানিয়ে নিয়েছে’- (তাওবাহঃ ৩১)।
হাদীসে আছে যে, হযরত আদী বিন হাতিম ঈসায়ী ছিলেন। পরে তিনি নবীর দরবারে হাজির হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি নবী(সা)- কে উপরোক্ত আয়াতটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে বলেন, আলেম-পীর-দরবেশকে খোদা বানাবার যে অভিযোগ আমাদের উপর করা হয়েছে, তার অর্থ কি? নবী(সা) বলেন, এ কথা কি ঠিক নয় যে, যা কিছু এসব লোক হারাম গণ্য করতো তা তোমরা হারাম বলে মেনে নিতে এবং যা তারা হালাল গণ্য করতো তা তোমরা হালাল বলে মেনে নিতে? হযরত আদী(রা) বলেন, হ্যাঁ, তাতো আমরা অবশ্যই করতাম।
নবী(সা) বলেন, এতেই তাদেরকে খোদা বানানো হয়।
এর থেকে জানা গেল, আল্লাহর সনদ ব্যতীত যারা মানব জীবনের জন্যে হালাল হারামের সীমারেখা নির্ধারণ করে তারা প্রকৃতপক্ষে নিজেরা খোদায়ীর আসনে সমাসীন হয়। যারা তাদের এ শরীয়ত প্রণয়ন মেনে নেয়, তারা তাদেরকে খোদা বানিয়ে নেয়।
যিনি যতো বড়োই হোন না কেন, তাঁর কোন কথা বা সিদ্ধান্ত যাচাই করার মাপকাঠি আল্লাহ ও তাঁর রসূল। যে কথা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের কথার বিপরীত অথবা কথার মূল ভাবধারার সাথে সামঞ্জস্যশীল নয় তা প্রত্যাখ্যানযোগ্য। এ ধারণা বিশ্বাস মানব সমাজকে বহু দলে উপদলে বিভক্ত করেছে এবং ফিৎনা-ফাসাদ সৃষ্টি করেছে।
তৃতীয় মৌলিক কারণ হলো, চরম ইসলাম-বিরোধী পরিবেশ। কোন একটি দেশ, জনপদ এমনকি কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অথবা ছাত্রাবাসের পরিবেশ যদি এমন হয় যে, সেখানকার সকলেই ইসলাম-বিরোধী, সেখানে শুধু ইসলাম-বিরোধী সাহিত্য ও পত্র-পত্রিকাই পরিবেশন করা হয়, ইসলাম-বিরোধী মন-মানসিকতা তৈরির প্রশিক্ষণ দেয়া হয়, তাহলে এমন পরিবেশে কেউ ইসলামের উপরে অবিচল থাকতে পারে না। এ পরিবেশে যুব সমাজের মন থেকে ধর্ম, খোদা ও আখেরাতের বিশ্বাসকে নড়বড়ে করার জন্যে তাদেরকে বিপরীত লিঙ্গের সাথে অবাধ মেলামেশার, গলাগলি, ঢলাঢলি করার সকল প্রকার সামগ্রীর যোগান দেয়া হয়।। এভাবে প্রাথমিক পর্যায়ে তাদের নৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙ্গে চুরমার করা হয়। এর ফলে পরবর্তী কার্যক্রম তারা সহজেই এবং আগ্রহ সহকারে গ্রহণ করতে পারে। এ কথাগুলো নিছক মানসলোকের কোন কল্পিত কাহিনী নয়। রাশিয়ার মতো কমিউনিস্ট দেশগুলোতে এসব কার্যক্রমই গ্রহণ করা হয়।
তারপর রাশিয়ার বাইরে যেসব অকমিউনিস্ট দেশে কমিউনিজমের চিন্তাধারা ও আন্দোলন রপ্তানি করা হয়, সেখানে সীমিত আকারে হলেও একই কায়দায় কার্যক্রম শুরু করা হয়। কোথাও প্রকাশ্যে, কোথাও গোপনে। তবে কাজের টেকনিক, কর্মী রিক্রুট ও তাদের প্রশিক্ষণ যথারীতি চলে। যুব সমাজকে নানান ছলেবলে-কৌশলে আয়ত্তে আনার চেষ্টা করা হয়। তার জন্যে রাশিয়া থেকে সকল প্রকার সাহায্য-সহযোগিতা করা হয়। এভাবে ক্রমশ নতুন দেশে কমিউনিস্ট শাসন কায়েম করা হয়। তাদের ফাঁদের সর্বশেষ শিকার আফগানিস্তান।
কোথাও কমিউনিস্ট শাসন কায়েম হলে বাক-স্বাধীনতা ও চিন্তার স্বাধীনতা বিলুপ্ত হয়। জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেক স্তব্ধ হয়ে যায়। কেউ বুদ্ধির সদ্ব্যবহার করতে চাইলেও তার কোন উপায় নেই। স্বেচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় কমিউনিস্ট শাসকদের মানসিক দাসত্ব মেনে নিতে হয়।
আম্বিয়ায়ে কেরামের দাওয়াত
উপরের আলোচনায় একথা সুস্পষ্ট হয়েছে যে, আল্লাহতায়ালা মানুষকে যে জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেক দিয়েছেন, তার সদ্ব্যবহার সকলে করে না এবং করতে জানেও না। ফলে তার ভয়াবহ পরিণাম মানুষকে ভোগ করতে হয়। মানুষের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে নানান মানবিক দুর্বলতাও আছে। মহান আল্লাহতায়ালা মানুষকে অসহায় অবস্থায় দেখে নীরব থাকতে পারেন না। ব্যাপারটি এমন নয় যে, ইসলাম ও জাহেলিয়াতের এ দ্বন্দ্ব-সংগ্রামে সত্যের জয়লাভের জন্যে যতো প্রকারের চেষ্টা-তদবীর হতে পারে তার দায়িত্ব মানুষের বুদ্ধি-বিবেক ও স্বাভাবিক যোগ্যতার উপরেই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। মানুষ তার বুদ্ধিবৃত্তিক চিন্তা-ভাবনা করে সব সময়ে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারে না। কারণ তার জ্ঞান ও চিন্তার জগত অতি ক্ষুদ্র ও সীমিত। চিন্তার একপর্যায়ে তার গতিপথ রুদ্ধ হয়ে যায়। তখন সে অসহায়ত্ব অনুভব করে এবং ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। মানবজাতির অনেক চিন্তানায়ক সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে নতুন নতুন দর্শন ও মতবাদ আবিষ্কার করেছেন যা মানুষের জীবনে অকল্যাণ ব্যতীত কল্যাণ বয়ে আনতে পারে নি। এ জন্যে দয়াময় আল্লাহতায়ালা মানুষের প্রতি অত্যন্ত দয়াপরবশ হয়ে তাঁর পক্ষ থেকে অভ্রান্ত জ্ঞান পরিবেশনের ব্যবস্থা করেছেন। একেই বলে ওহীর জ্ঞান বা ঐশীজ্ঞান। এ জ্ঞান তিনি মানুষকে সরাসরি পরিবেশন করেন না, সমাজের সবচেয়ে ভালো মানুষটিকে তিনি বেছে নেন এবং ওহীর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সকল জ্ঞান দান করেন। মানুষকে সুস্থ প্রকৃতি ও জ্ঞানবুদ্ধি দেয়ার পর এ এক অতিরিক্ত জ্ঞান। মানুষের ভেতর ও বাইরে থেকে বহু চিন্তাচেতনা, ভয়ভীতি, প্ররোচনা এবং তার ষড়রিপুর প্রভাব যখন তাকে পথভ্রষ্ট করার চেষ্টা করে তখন এই অতিরিক্ত জ্ঞান তার সহায়তায় এগিয়ে আসে এবং সঠিক পথ প্রদর্শন করে। অবশ্যি এ অতিরিক্ত জ্ঞান প্রত্যাখ্যান করা তার জন্যে অতি দুর্ভাগ্যজনক হলেও তা করার স্বাধীনতাও তাকে দেয়া হয়েছে। আল্লাহতায়ালা মানুষকে এভাবে পরীক্ষায় নিক্ষেপ করে তা উত্তীর্ণ হওয়ার জন্যে উপায়-উপকরণও দান করেছেন যাতে করে সে মানুষের সর্বোচ্চ মর্যাদা লাভ করতে পারে।
উপরে বর্ণিত এ অতিরিক্ত জ্ঞানকে ওহীর জ্ঞান বলা হয়েছে। সেই সাথে এ ওহীর বাহকও পাঠিয়েছেন, যিনি অন্যান্য মানুষের মতোই একজন মানুষ। তিনি ওহীর জ্ঞান মানুষের মধ্যে পরিবেশন করবেন। তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করবেন এবং স্বয়ং তার বাস্তব জীবন দিয়ে সে জ্ঞান কার্যকর করে দেখাবেন। ওহীবাহক এ ব্যক্তিকে নবী বা রসূল বলা হয়। মানুষকে পথ প্রদর্শন, তাদের সত্যিকার মানবীয় চরিত্র গঠন এবং তাদের জীবনকে সুখী ও সুন্দর করার জন্যে যুগে যুগে দুনিয়ার বুকে নবী রসূলগণ প্রেরিত হয়েছেন।
নবীগণের দাওয়াত ও জাহেলিয়াতের দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ
ইসলাম ও জাহেলিয়াতকে সত্য ও মিথ্যা এবং আলোক ও অন্ধকারের সাথে তুলনা করা হয়েছে। এ সত্য ও মিথ্যা, আলোক ও অন্ধকারের যেমন এক মুহূর্তের জন্যেও সহাবস্থান সম্ভব নয়, তেমনি ইসলাম ও জাহেলিয়াতের সহাবস্থান কিছুতেই সম্ভব নয়। তাই যুগে যুগে যখন নবীগণের মাধ্যমে মানুষের কাছে ইসলামের দাওয়াত, সত্যের দাওয়াত এসেছে, জাহেলিয়াত তাকে বরদাশত করতে পারে নি। তাই মানব জাতির সমগ্র ইতিহাসই হচ্ছে ইসলাম ও জাহেলিয়াতের তথা সত্য ও মিথ্যার দ্বন্দ্বসংগ্রাম।
আল্লাহর মহিমান্বিত নবীগণই বিভ্রান্ত পথভ্রষ্ট ও অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিমজ্জিত মানবজাতির জন্যে সত্যসঠিক পথের আলোকবর্তিকা নিয়ে আসেন। সেজন্যে জাহেলিয়াত তাদের পথে চরম প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। শুধু তাই নয়, নবীগণ জাহেলিয়াতের পতাকাবাহীদের হাতে চরমভাবে নির্যাতিত হন এবং অনেকে প্রাণও হারান। সংক্ষেপে নবীদের দাওয়াত তথা ইসলাম ও জাহেলিয়াতের দ্বন্দ্ব-সংঘাতের কিছু বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হলো।
হযরত নূহ (আ)
হযরত নূহের (আ) সময় থেকেই আমরা মানব জাতির ইতিহাস কিছুটা জানতে পারি। মানবজাতির এক সুদীর্ঘকালের কোন মানব রচিত ইতিহাস নেই। এ সুদীর্ঘ যুগকে প্রাগৈতিহাসিক যুগ বলে। তবে এ যুগের নবীগণের ইতিহাস আসমানী কিতাবগুলোতে বর্ণনা করা হয়েছে এবং অতি নির্ভরযোগ্য বর্ণনা কুরআনে করা হয়েছে। হযরত নূহ (আ) তাঁর জাতিকে সম্বোধন করে বলেন-
“সে (নূহ) বললো, হে আমার জাতির লোকেরা! আমি তোমাদের জন্যে পরিষ্কার ভাষায় সাবধানকারী (একজন নবী)। (তোমাদেরকে এ কথা বলে সাবধান করে দিচ্ছি যে) আল্লাহর বন্দেগী কর ও তাঁকে ভয় কর এবং আমার অনুসরণ কর। আল্লাহ তোমাদের গুনাহ মাফ করে দেবেন এবং একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখবেন। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর নির্দিষ্ট সময় যখন আসে তখন আর তাকে রোধ করা যায় না। (এসব) যদি তোমরা জানতে তাহলে কতই না ভালো হতো”- (নূহঃ ২-৪)।
তাঁর দাওয়াত সুস্পষ্ট ও ন্যায়সঙ্গত। যে আল্লাহ মানুষকে পয়দা করেছেন এবং তার জন্ম সূচনা থেকে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত প্রত্যেকটি প্রয়োজন পূরণ করছেন- হুকুম শাসন তাঁরই মেনে চলা অত্যন্ত স্বাভাবিক ও ন্যায়সঙ্গত। কিন্তু তাঁর জাতির সমাজপতি ও সাধারণ লোকেরা তাঁর এ দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করে। কিন্তু হযরত নূহ (আ) অসাধারণ ধৈর্য্য সহকারে তাঁর দাওয়াতী কাজ অব্যাহত রাখেন। এক সুদীর্ঘকাল যাবত অর্থাৎ সাড়ে ন’শ’ বছর যাবত তিনি তাদেরকে সত্যের দিকে আহবান জানাতে থাকেন।
তিনি তাদেরকে এক সুদূর ভবিষ্যতের অর্থাৎ মৃত্যুর পর জীবনের কল্যাণের নিশ্চয়তাই দেননি, দুনিয়ার জীবনের কল্যাণের কথাও বলেছেন।
‘আমি বলেছি, তোমরা তোমাদের প্রভুর নিকট ক্ষমা চাও। তিনি অবশ্যই বড়ো ক্ষমাশীল। তিনি তোমাদের জন্য আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করবেন। তোমাদেরকে ধনদৌলত ও সন্তানাদি দিয়ে ধন্য করবেন। তোমাদের জন্যে বাগ-বাগিচা তৈরি করে দেবেন এবং ঝর্ণা প্রবাহিত করবেন’- (নূহঃ ১০-১৪)।
দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ লাভের জন্য তিনি একথা বলেন, তোমাদের মিথ্যা ও স্বরচিত খোদাদের পরিহার করে এক আল্লাহর বন্দেগী কর। জাতির সমাজপতিগণ তাঁর এ দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করে জনসাধারণের প্রতি কঠোরভাবে নির্দেশ জারি করে,
‘তোমাদের মাবূদদেরকে তোমরা কিছুতেই পরিত্যাগ করবে না। পরিত্যাগ করবে না ওয়াদ, সুয়া, ইয়াগুস, ইয়াউক ও নসরকে’- (নূহঃ ২৩)।
জবাবে তারা হযরত নূহকে (আ) বলে-
‘আমরা তোমাকে সুস্পষ্ট গোমরাহিতে লিপ্ত দেখতে পাচ্ছি’- (আ’রাফঃ ৬০)।
জাতির তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের দৃষ্টিতে এক খোদাকে মেনে নেয়া মারাত্মক ভুল ও গোমরাহি। তাদের কথা-
যদিও এ বিশ্বজগত এক খোদার তৈরি, কিন্তু এ পরিচালনা করছে বহু খোদা। সে জন্যে অন্য খোদাদেরও এ অধিকার আছে যে, তাদেরও পূজা-উপাসনা করতে হবে। তাদের বুদ্ধিজীবী ও সমাজপতিগণ- যারা নূহের (আ) কথা মানতে অস্বীকার করেছিল, বললো- ‘আমাদের দৃষ্টিতে তুমি আমাদেরই মতো একজন মানুষ ছাড়া তো কিছু নও। আমরা আরো দেখছি যে, আমাদের মধ্যে যারা একেবারে হীন ও নিকৃষ্ট, তারা কোনপ্রকার ভাবনা-চিন্তা না করেই তোমার পথ ধরেছে। আমরা তো এমন কিছু দেখতে পাই না যে, তোমরা আমাদের থেকে ভালো ও অগ্রসর। বরং তোমাদেরকে মিথ্যাবাদীই মনে করি’- (হুদঃ ২২)।
সে সময়ে জনগণকে শাসন-শোষণ করতো এসব সর্দার-সমাজপতিরাই। মানুষের রুজি-রোজগারের চাবিকাঠিও তাদের হাতে ছিল। বাগবাগিচা, ক্ষেতখামার ও ব্যবসা-বাণিজ্যের মালিকও তারা ছিল। তারা দুনিয়ার ভোগ-বিলাসে নিমগ্ন ছিল। তাদের দাপটে কেউ নবীর দাওয়াত গ্রহণের সাহস করতো না। করলে তাদের উপর নানা জুলুম উৎপীড়নের পাহাড় ভেঙ্গে পড়তো। কতিপয় উৎপীড়িত মজলুম মানুষ- সংখ্যায় অতি নগণ্য- হযরত নূহের দাওয়াত কবুল করেছিল। সমাজপতিরা এদেরকে ঘৃণার চোখে দেখত। যা হোক, হযরত নূহ (আ) তাদেরকে নানানভাবে মিষ্টি ভাষায় যুক্তিসহকারে বুঝাবার চেষ্টা করতে থাকেন।
‘সে বললো, হে আমার জাতির লোকেরা! একটু চিন্তা ভাবনা করে তো দেখ যে, যদি আমি আমার রবের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট সাক্ষ্যের উপরে কায়েম হয়ে থাকি এবং তারপর তিনি যদি আমাকে তাঁর বিশেষ অনুগ্রহ দ্বারা ধন্য করে থাকেন এবং তোমরা দেখতে না পাও, তাহলে আমার কাছে এমন কি উপায় আছে যে, তোমরা মানতে চাও না এবং আমি বলপ্রয়োগে তোমাদের উপরে তা চাপিয়ে দেব? হে আমার জাতির ভাইবেরাদরগণ! আমি এ কাজের জন্যে তোমাদের কাছে কোন অর্থসম্পদ চাই না। আমার প্রতিদান তো আল্লাহর যিম্মায় রয়েছে। আমার কথা যারা মেনে নিয়েছে আমি তাদেরকে ধাক্কা দিতেও প্রস্তুত নই। তারা নিজেরাই তাদের রবের সামনে হাজির হবে। কিন্তু আমি দেখছি যে, তোমরা জাহেলিয়াতের মধ্যেই ডুবে আছ’- (হুদঃ ২৮-২৯)।
সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত বার বার বিভিন্নভাবে তাদের কাছে সত্যের দাওয়াত পেশ করার পরও তাদের হঠকারিতা, পদমর্যাদার অহংকার এবং সমাজের উপর তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি কিছুতেই সত্যের প্রতি তাদেরকে আকৃষ্ট করতে পারেনি। হযরত নূহ যখন তাঁর রেসালাত মেনে নেবার আহবান জানান, তখন তার জবাবে তারা তা অতি বিস্ময় প্রকাশ করে প্রত্যাখ্যান করে। তারা বলে, আচ্ছা যদি মেনে নেয়াই যায় যে, মাবুদ একজনই এবং মেনেও নিলাম যে, তিনি মানুষের জন্যে একজন পয়গম্বর পাঠাতে চান, তাহলে এটা কি করে হতে পারে যে, আমাদেরই মতো একজন মানুষকে তিনি পয়গম্বর করে পাঠাবেন? পাঠাতে চাইলে তো তাঁর নিকটস্থ ফেরেশতাকে পয়গম্বর হিসেবে পাঠাতে পারতেন।
তার জাতির যেসব সমাজপতিরা তার দাওয়াত মানতে অস্বীকার করে তারা বলেঃ ‘এ ব্যক্তি তোমাদেরই মতো একজন মানুষ ছাড়া তো আর কিছু নয়। তার উদ্দেশ্য হলো, সে তোমাদের উপর তার অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চায়। আল্লাহর কাউকে পাঠাতে হলে তো ফেরেশতা পাঠাতেন। এ কথা তো আমরা আমাদের বাপ-দাদার আমলে শুনিনি (যে মানুষ রসূল হয়ে আসে)। আর কিছু না, ব্যস, এ লোকটাকে কিছু পাগলামিতে পেয়েছে। আরও কিছুদিন দেখ (হয়তো পাগলামি সেরে যেতে পারে)’- (মুমেনূনঃ ২৩-২৪)।
তাদের এ যুক্তির বলে তারা শুধুমাত্র হযরত নূহের নবুওতকেই অস্বীকার করলো না, বরং সমগ্র নবী পরম্পরাকেই তারা অস্বীকার করলো। কারণ, আল্লাহতায়ালা যতো নবী-রসূল পাঠিয়েছেন, তাঁরা সকলেই মানুষ ছিলেন।
এক পর্যায়ে তারা হযরত নূহকে (আ) ভয়ানকভাবে শাসিয়ে দেয়।
‘হে নূহ! তুমি যদি এসব কাজ থেকে বিরত না হও, তাহলে আমরা তোমাকে পাথর মেরে মেরে খতম করে দেব’- (শুয়ারাঃ ১১৬)।
তারপর হযরত নূহ (আ) এবং তাঁর মুষ্টিমেয় অনুসারীদের উপর যে নির্যাতন শুরু হয়েছিল তা সহজেই অনুমান করা যায়। কারণ, একটা গোটা জাতির মধ্যে অর্ধশত লোকও ইসলামের দাওয়াত কবুল করেনি।
অবশেষে ইসলাম ও জাহেলিয়াতের দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে, যখন নূহ নবী খোদার আশ্রয় প্রার্থনা করতে বাধ্য হন।
‘আর নূহ বললোঃ হে আমার খোদা! এ কাফেরদের মধ্য থেকে এ জমিনে বসবাসকারী একজনকেও ছেড়ে দিও না। তুমি যদি এদেরকে ছেড়ে দাও, তাহলে এরা তোমার বান্দাহদেরকে গোমরাহ করে দেবে। আর এদের বংশে যারাই জন্মগ্রহণ করবে তারা কট্টর পাপাচারী কাফেরই হবে’- (নূহঃ ২৬-২৭)।
আল্লাহতায়ালা তার প্রিয় নির্যাতিত নবীর দোয়া কবুল করেন এবং এক ভয়াবহ বন্যা দিয়ে গোটা জাতিকে ডুবিয়ে ধ্বংস করে দেন।
‘অবশেষে যখন আমার হুকুম এসে গেল এবং সে চুলাটি উথলে উঠলো, তখন আমি বললাম, প্রত্যেক রকমের জন্তু জানোয়ার এক এক জোড়া করে নৌকায় তুলে নাও। তোমার পরিবারের লোকদেরকেও এতে সওয়ার করে নাও- শুধু তাদের ছাড়া যাদেরকে আগেই চিহ্নিত করা হয়েছে। তাদেরকেও (নৌকায়) বসিয়ে নাও যারা ঈমান এনেছে। আর নূহের সাথে ঈমানদারদের সংখ্যা ছিল খুব নগণ্য’- (হুদঃ ৪০)।
নূহের মহাপ্লাবনের কথা সর্বজনবিদিত। কথিত আছে সর্বমোট চল্লিশজন- তাঁর পরিবারের লোকজনসহ অথবা ছাড়া- আল্লাহর এ গজব থেকে বেঁচে যায়। প্রায় একহাজার বছর ইসলাম ও জাহেলিয়াতের সংঘাতের পর জাহেলিয়াত মূলোৎপাটিত হয়।
কুরআন পাকে হযরত নূহ (আ)-এর আন্দোলনের বিশদ বিবরণ আছে। এখানে মাত্র সারসংক্ষেপ তুলে ধরা হলো।
আদ জাতি
ইতিহাস বিশারদগণ বলেন যে, হযরত নূহ (আ) এমন অঞ্চলে তাঁর দাওয়াতী কাজ চালান যাকে বর্তমানে ইরাক বলে। তাঁর তিরোধানের পর মানুষের সংখ্যা বর্ধিত হতে থাকে এবং তারা চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। তারা নবীর শিক্ষাদীক্ষা ভুলে পুনরায় গোমরাহীতে লিপ্ত হয়। নূহের জাতির পরে যে জাতি খুবই শক্তিধর ও প্রভাব প্রতিপত্তিশালী হয় তা হলো আদ জাতি। আদ জাতি সম্পর্কে আরবের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা অবহিত ছিল। তাদের শৌর্যবীর্যের কথা যেমন আরববাসীদের জানা ছিল, তেমনি তাদের ধ্বংসের বিবরণও তাদের জানা ছিল। তারা উন্নতির উচ্চশিখরে আরোহন করার পর আবার তাদের সভ্যতা-সংস্কৃতিসহ ধ্বংস গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হয়। তাদের বাস ছিল আহকাফ অঞ্চলে যা হিজায, ইয়ামেন ও ইয়ামামার মধ্যবর্তী ‘রাবউল খালী’-এর দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত ছিল। তাদের সম্পর্কে কুরআনের বর্ণনা নিম্নরূপ।
আদ জাতির হেদায়াতের জন্য আল্লাহতায়ালা হযরত হুদকে (আ) প্রেরণ করেন। জাহেলিয়াতের কালো অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল এ জাতি। হযরত হুদের (আ) ইসলামী দাওয়াত পেশ করায় উভয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাতের সূচনা হয়, তাদের কাছে দ্বীনে হকের যে কথাই বলা হতো তা ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে উড়িয়ে দেয়া হতো। নূহের জাতি যে ধরনের আপত্তি উত্থাপন করে কূটযুক্তির জাল বিস্তার করে নবীর দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করে, আদ জাতির লোকেরাও তা-ই করে।
‘তুমি কি আমাদের নিকটে এ জন্যে এসেছো যে, আমরা এক খোদার বন্দেগী করব এবং ঐ সব খোদাদেরকে পরিহার করব, যাদের বন্দেগী আমাদের বাপ-দাদা করে এসেছে?’- (আ’রাফঃ ৭০)।
হযরত হুদের (আ) সাথে আদ জাতির এ সংঘাত-সংঘর্ষ চলতে থাকে। আল্লাহর নবী হুদ (আ) তাদেরকে অত্যন্ত দরদের সাথে স্থায়ী কল্যাণের দিকে আহবান জানাতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত তারা আল্লাহর প্রিয় নবী যে সত্য নবী তা প্রমাণ করার দাবি জানায়।
‘আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি যদি সত্যবাদী হয়ে থাক, তাহলে তুমি আমাদের যে আজাবের হুমকি দিচ্ছ, তা নিয়ে এস’- (আহকাফঃ ২২)।
তারা বার বার আজাবের দাবি করাতে তাদের ভাগ্যে তা-ই ঘটলো।
‘আদকে ধ্বংস করা হয়েছে এক প্রচণ্ড সাইক্লোন বা ঘূর্ণিবাতাস দিয়ে। আল্লাহ তাদের উপর তা (তুফান) ক্রমাগত সাতরাত ও আটদিন পর্যন্ত চাপিয়ে রাখেন। তুমি (সেখানে থাকলে) দেখতে পেতে তারা সেখানে এমনভাবে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে আছে, যেমন পুরাতন শুকনো খেজুর গাছের কাণ্ডসমূহ পড়ে থাকে। এখন তাদের মধ্যে কেউ কি বাকি আছে দেখতে পাও’- (আল-হাক্কাহঃ ৬-৮)।
এভাবে দুনিয়ার বুক থেকে আদ জাতির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে গেল। তবে হযরত হুদের (আ) সাথে অবশ্যই কিছু নেক লোক ছিল যারা তাঁর দাওয়াত কবুল করে আল্লাহর সৎ বান্দাহ হিসেবে জীবন যাপন করছিল। তাদেরকে আল্লাহ এ ভয়ংকর প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে বিচিত্র উপায়ে রক্ষা করেন।
‘এবং আদের জন্যে আমরা তার ভাই হুদকে পাঠালাম। সে বললো, হে আমার জাতির ভাইয়েরা! আল্লাহর বন্দেগী কর, তিনি ছাড়া তোমাদের আর কেউ ইলাহ নেই। তোমরা শুধু মিথ্যা রচনা করে রেখেছো। হে আমার জাতির ভাইয়েরা! এ কাজের জন্যে তোমাদের কাছে আমি কোন প্রতিদান চাই না। আমার প্রতিদান তো তাঁর যিম্মায় যিনি আমাকে পয়দা করেছেন। তোমরা কি একটু বিবেক-বুদ্ধিসহ কাজ কর না? হে আমার জাতির লোকেরা! তোমাদের রবের কাছে ক্ষমা চাও! তারপর তাঁর দিকে ফিরে যাও, তিনি তোমাদের জন্যে আসমান থেকে মুষলধারে পানি বর্ষণ করবেন। তোমাদের বর্তমান শক্তি আরো বাড়িয়ে দেবেন। অপরাধী হয়ে (বন্দেগী থেকে) মুখ ফিরিয়ে রেখো না।’
‘তারা জবাবে বলে, হে হুদ! তুমি আমাদের নিকটে কোন সুস্পষ্ট সাক্ষ্য নিয়ে আসনি এবং তোমার কথামতো আমরা আমাদের খোদাদের ছাড়তে পারি না এবং তোমাদের উপর আমরা ঈমানও আনব না। আমরা তো মনে করি যে, তোমার উপর আমাদের কোন খোদার অভিশাপ লেগেছে।’
‘হুদ বলে, আমি আল্লাহর সাক্ষ্য পেশ করছি এবং তোমরা সাক্ষী থাকো, এই যে তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে অন্যান্যকে খোদায়ীতে শরীক গণ্য করে রেখেছো, এর প্রতি আমি অসন্তুষ্ট। তোমরা সবাই মিলে আমার বিরুদ্ধে যা করার তাতে কিছু কমতি রেখো না। এবং আমাকে সামান্য অবকাশও দিও না। আমার ভরসা তো আল্লাহর উপরে, যিনি আমার রব এবং তোমাদেরও। কোন প্রাণী এমন নেই যার মাথা তাঁর মুঠোর মধ্যে নেই। নিঃসন্দেহে আমার খোদা সোজা পথের উপর আছেন। তোমরা যদি মুখ ফিরিয়ে নিতে চাও, তো ফিরিয়ে নাও। যে পয়গামসহ আমাকে তোমাদের কাছে পাঠানো হয়েছে, তা আমি তোমাদের কাছে পৌঁছিয়ে দিয়েছি। এখন আমার রব তোমাদের স্থলে অপর জাতিকে উঠাবেন। আর তোমরা তাঁর কোনও ক্ষতি করতে পারবে না। আমার খোদা নিশ্চিতই সব কিছুই নিয়ন্ত্রণকারী। পরে যখন আমাদের ফরমান এসে গেল, তখন আমরা আমাদের রহমতের সাহায্যে এবং তার সাথে যারা ঈমান এনেছিল তাদেরকে নাজাত দিলাম এবং কঠিন আজাব থেকে তাদেরকে বাঁচালাম।
এই হচ্ছে আদ। তাদের খোদার আয়াতকে তারা অমান্য করলো এবং নবী-রসূলের কথাও তারা মানলো না। এবং সত্য দ্বীনের প্রবল পরাক্রান্ত দুশমনের তারা অনুসরণ করলো। শেষ পর্যন্ত এ দুনিয়াতেও তাদের উপর অভিসম্পাত হলো এবং কিয়ামতের দিনও। জেনে রাখ, আদ তাদের রবকে অমান্য করলো এবং দূরে নিক্ষেপ করা হলো আদ অর্থাৎ হুদের জাতির লোকদেরকে’- (হুদঃ ৫৪-৬০)।
হযরত নূহ (আ)-এর জাতির ধ্বংসের পর আল্লাহতায়ালা হুদ জাতিকে উন্নতির উচ্চশিখরে আরোহণ করার সুযোগ দান করেন। তৎকালে শৌর্য-বীর্যের দিক দিয়ে তাদের সমতুল্য আর কেউ ছিল না। শুধু খোদাদ্রোহিতার অপরাধে তাদেরকে দুনিয়ার বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হয়।
সামূদ জাতি
আদ জাতির ধ্বংসের পর যাদেরকে তাদের নেক আমলের জন্যে আল্লাহতায়ালা রক্ষা করেছিলেন, তারা হযরত হুদ (আ)-এর শিক্ষাদীক্ষা অনুযায়ী জীবন যাপন করতে থাকে। কিন্তু কিছুকাল অতিবাহিত হওয়ার পর তারা জাহেলিয়াতের খপ্পরে পড়ে পথভ্রষ্ট হয়ে যায়। তাদের হেদায়েতের জন্যে আল্লাহতায়ালা হযরত সালেহকে (আ) প্রেরণ করেন। আবার ইসলাম ও জাহেলিয়াতের দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ শুরু হয়।
আরবের প্রাচীনতম জাতিসমূহের মধ্যে সামূদ দ্বিতীয় এবং আদ জাতির পর তারা ছিল সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। কুরআন নাযিলের পূর্বে তাদের কেচ্ছাকাহিনী আরবের আবাল বৃদ্ধ বনিতার মুখে শোনা যেত। জাহেলিয়াতের যুগের কবিতা ও বক্তৃতা-ভাষণের মধ্যে তাদের উল্লেখ করা হতো। আসিরিয়ার শিলালিপিতে এবং গ্রীস, আলেকজান্দ্রিয়া ও রোমের প্রাচীন ইতিহাসে তাদের উল্লেখ পাওয়া যায়। আদ জাতির ধ্বংসের পর তাদের মধ্যে যারা বেঁচে গিয়েছিল, তাদের বংশধর হযরত ঈসা (আ)-এর জন্মের কিছুকাল পূর্ব পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। রোমীয় ঐতিহাসিকগণ বলেন, এসব লোক রোমীয় সৈন্যবাহিনীতে ভর্তি হলে নাবতীদের বিরুদ্ধে লড়াই করে যাদের সাথে প্রাচীন শত্রুতা ছিল। তাদের আবাসস্থল ছিল উত্তর-পশ্চিম আরবের ঐসব অঞ্চলে যা আজও আল-হিজর নামে প্রসিদ্ধ। বর্তমানে মদীনা ও তাবুকের মধ্যবর্তী হেজাজ রেলওয়ের একটি স্টেশন আছে যাকে মাদায়েনে সালেহ বলা হয়। এ স্থানটি ছিল সামূদ জাতির কেন্দ্রীয় বাসস্থল। এখনও সেখানে হাজার হাজার একর এলাকা জুড়ে পাহাড়ী দালান কোঠার ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাওয়া যায়- যা তারা পাহাড় খোদাই করে তৈরি করেছিল। এসব দেখলে মনে হয় এ শহরের অধিবাসীর সংখ্যা চার পাঁচ লক্ষের কম ছিল না। কুরআন নাযিলের যুগে হেজাজের বাণিজ্যিক কাফেলা এসব ধ্বংসাবশেষের পাশ দিয়ে অতিবাহিত হয়। নবী আকরাম (সা) তাবুক অভিযানকালে এ দিক দিয়ে পথ অতিক্রমকালে এ শিক্ষণীয় ধ্বংসাবশেষগুলো দেখান এবং শিক্ষাগ্রহণ করতে বলেন। একস্থানে একটি কূপ চিহ্নিত করে তিনি বলেন, এই কূপ থেকে হযরত সালেহ (আ) এর উটনী পানি পান করতো। তিনি মুসলমানদেরকে অন্য কূপ থেকে পানি পান না করে এই একটি কূপ থেকে পানি পানের নির্দেশ দেন। নবী (সা) একটি উপত্যকা দেখিয়ে দিয়ে বলেন যে, এখান থেকে উটনী পানি পান করতে আসতো। এ স্থানটি এখনো ‘ফজ্জুন্নাকাহ’ নামে খ্যাত।
হযরত সালেহ (আ) তাদের সামনে একই দাওয়াত পেশ করেন, যা সকল নবী-রসূলের মৌলিক দাওয়াত ছিল।
‘এবং সামূদ জাতির প্রতি আমরা তাদের ভাই সালেহকে পাঠালাম। সে বললো, হে আমার জাতির লোকেরা! তোমরা একমাত্র আল্লাহর বন্দেগী কর, তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন ইলাহ নেই’- (আ’রাফঃ ৭৩)।
উল্লেখ্য যে, নবুওতের পূর্বে হযরত সালেহ (আ) তাঁর জাতির অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন এবং সকলেই তাঁর উপরে তাদের যাবতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা ন্যস্ত করেছিল। ইসলামের দাওয়াত পেশ করার পর তিনি তাদের ঘৃণার পাত্র হয়ে পড়লেন। তাঁর দাওয়াতের জবাবে তারা বলে-
‘হে সালেহ! গতকাল পর্যন্ত তোমার উপর আমরা বড়ই আশা পোষণ করেছিলাম। (কিন্তু আজ এ কি হলো যে) তুমি আমাদেরকে ঐসব মাবুদদের পূজা-উপাসনা করতে নিষেধ করছ, যাদেরকে আমাদের পূর্ব-পুরুষগণ পূজা করতো?’- (হূদঃ ৬৩)।
তারা তাওহীদের দিকে দাওয়াতকেও একটা প্রতারণা বলে গণ্য করে এবং এ বিষয়ে এভাবে মন্তব্য করে-
‘তুমি নিছক যাদু প্রভাবিত। তুমি আমাদেরই মতো একজন মানুষ ব্যতীত কিছু নও’- (শুয়ারাঃ ১৫৪)।
একই রকমের ওজর-আপত্তি ও অভিযোগ তারা করে যা নূহ এবং হুদের জাতি করেছিল। হযরত সালেহ (আ) বহুভাবে তাদেরকে নসিহত করেন এবং ভয়াবহ পরিণাম থেকে সাবধান করে দেন। কিন্তু তারা তাঁর প্রত্যেকটি কথা প্রত্যাখ্যান করে। অবশেষে তারা ভয়াবহ পরিণামের সম্মুখীন হয়-
‘সাবধানবাণীকে সামূদ জাতি মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিল। তারা বললো, এক ব্যক্তি, যে আমাদেরই মতো একজন, তার পেছনে আমরা চলবো? তার অনুসরণ করলে তার অর্থ এই হবে যে, আমরা পথভ্রষ্ট হয়েছি এবং আমরা বিবেকহীন হয়ে পড়েছি। আমাদের মধ্যে এই এক ব্যক্তিই কি ছিল, যার উপর খোদার যিকর নাযিল করা হয়েছে? না, বরং সে ভয়ানক মিথ্যাবাদী ও আত্মবিভ্রান্ত। (আমরা আমাদের নবীকে বললাম) কালই তারা জানতে পারবে যে, কে ভয়ানক মিথ্যাবাদী ও স্বয়ংভ্রান্ত। আমরা উটনীকে তাদের জন্যে ফেৎনা হিসাবে পাঠাব। একটু সবর কর, তাদের কি পরিণাম হয় দেখ। তাদেরকে জানিয়ে সতর্ক করে দাও যে, পানি এদের এবং উটনীর মধ্যে ভাগ করে দেয়া হবে এবং প্রত্যেকে নিজেদের নির্দিষ্ট দিনে পানি পান করতে আসবে। সবশেষে তাদের এক (দুর্বৃত্ত) লোককে তারা ডাকলো। সে কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করলো এবং উটনীকে মেরে ফেললো। তারপর দেখ আমার আজাব ও হুঁশিয়ারী কত ভয়ংকর ছিল। আমরা তাদের উপর একটি মাত্র প্রচণ্ড ধ্বনি পাঠালাম এবং তারা খোয়াঁড়ওয়ালার নিষ্পেষিত ও চূর্ণবিচূর্ণ ভূষির মতো হয়ে গেল’- (আল-কাসাসঃ ২৩-৩১)।
কুরআন পাকের অন্যত্র বলা হয়েছে-
‘অতঃপর তারা সে উটনীকে মেরে ফেললো এবং পূর্ণ ঔদ্ধত্য সহকারে তাদের রবের আদেশ লংঘন করলো। তারপর তারা সালেহকে বললো, নিয়ে এসো সে আজাব যার হুমকি তুমি দিচ্ছ, যদি তুমি সত্যিই নবীগণের মধ্যে একজন হয়ে থাক। অবশেষে এক প্রলয়ংকরী বিপদ তাদেরকে গ্রাস করলো এবং তারা আপন আপন বাড়িতে উপুড় হয়ে পড়ে মরে রইলো। সালেহ একথা বলে তাদের জনপদ থেকে বেরিয়ে গেল, হে আমার জাতি! আমি আমার রবের পয়গাম তোমাদের কাছে পৌঁছিয়ে দিয়েছি এবং তোমাদের বড়ই মঙ্গল কামনা করেছি। কিন্তু কি করব, আমার এ উপদেশ, মঙ্গল কামনা তোমরা পছন্দ করলে না’- (আ’রাফঃ ৭৭-৭৮)।
লূত জাতি
হযরত সালেহের (আ) পর আরও কতিপয় নবীর আগমন হয় এবং প্রত্যেকের সাথে তাঁদের জাতির লোকেরা একই আচরণ করে। অর্থাৎ সত্যের দাওয়াত তারা প্রত্যাখ্যান করে। নবীগণকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করে এবং তাঁদের উপর নানানভাবে নির্যাতন চালাতেও দ্বিধাবোধ করেনি। অবশেষে হযরত লূত (আ)- এর আগমন হয়। পূর্ববতী নবীগণ যেসব বাধা বিঘ্ন, প্রতিবন্ধকতা, ঠাট্টা বিদ্রুপ ইত্যাদির সম্মুখীন হন, হযরত লূত (আ)-কেও সে সবের সম্মুখীন হতে হয়। উপরিন্তু তাঁকে এক অভিনব, বিস্ময়কর ও ঘৃণ্য নৈতিক মতবাদের মুকাবিলা করতে হয়। আর তা ছিল সমাজে প্রচলিত ব্যাপক সমকামিতা। তাদের মতবাদের সারমর্ম হলো, কর্মের স্বাধীনতাকে নৈতিক শৃঙ্খলে আবদ্ধ করা যেতে পারে না। লূত জাতি স্বাধীনতার এ পাশবিক মতবাদ দৃঢ় প্রত্য্যসহ গ্রহণ করে, যার ফলে তারা ঘৃণ্য নৈতিক পংকিলতায় নিমজ্জিত হয়েছিল। হযরত লূত (আ) শির্ক-কুফর খণ্ডনের সাথে সাথে তাদের এ ঘৃণ্য রুচিবোধেরও তীব্র সমালোচনা করেন। কিন্তু তারা তাঁর এসব কথায় মোটেই কর্ণপাত করে না।
“আর লূতকে আমরা পয়গম্বর বানিয়ে পাঠিয়েছি। তারপর স্মরণ কর, যখন সে তাঁর জাতির লোকদেরকে বললো, তোমরা কি এতোটা নির্লজ্জ হয়ে গিয়েছ যে, তোমরা এমন সব নির্লজ্জ কাজ করছ যা তোমাদের পূর্বে দুনিয়ায় আর কেউ করেনি? তোমরা নারীদের বাদ দিয়ে পুরুষের দ্বারা তোন্মাদের যৌন লালসা চরিতার্থ কর। তোমরা আসলে একেবারেই সীমালঙ্ঘনকারী। কিন্তু তার জাতির জবাব এছাড়া আর কিছু ছিল না, এসব লোকদেরকে বের করে দাও তাদের জনপদ থেকে; বড়ো পাক-পবিত্র হয়ে পড়েছে এরা”- (আ’রাফঃ ৮০-৮২)।
তাদের কথাটাই যেন এই, লূত ও তাঁর অনুসারীদের আমাদের এ কাজ পছন্দ না হয় তো না হোক। কিন্তু আমাদের কাজে বাধা দেবার কি অধিকার তাদের আছে?
চরিত্রবান হয়ে রুচিসম্মত জীবন যাপন করার যে নসিহত হযরত লূত (আ) করছিলেন, তা তাদের কিছুতেই সহ্য হচ্ছিল না, তাই তারা তাঁকে তাদের শহর থেকে বহিষ্কার করে দিতে মনস্থ করল। জাহেলিয়াতের ভ্রান্ত চিন্তাধারা ও মতবাদ হতভাগা জাতিকে সত্যের আলোক থেকে এতোটা দূরে নিক্ষেপ করেছিল এবং তাদের জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেককে এতোটা বিকল ও বিকৃত করে ফেলেছিল যে, তৌহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের দাওয়াতে তারা সাড়া দেবে কি করে? বরং সত্যের আহবানকারীকে তারা তাদের জীবনের শত্রু মনে করলো। সর্বাত্মক চেষ্টার পরও যখন তাদের কোন মানসিক পরিবর্তন হলো না, তখন আল্লাহতায়ালা তাঁর শাশ্বত নীতি অনুযায়ী তাদেরকে পাকড়াও করলেন এবং তাদেরকে দুনিয়ার বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিলেন।
এ জাতির ধ্বংসের বিবরণ কুরআন পাকে সন্নিবেশিত করা হয়েছে।
“(হে নবী মুহাম্মদ!) ইব্রাহীমের সম্মানিত মেহমানদের কাহিনী কি তোমার কাছে পৌঁছেছে? তারা তার কাছে গিয়ে বললো, তোমার প্রতি সালাম। সে বললো, তোমাদের প্রতিও সালাম। তার কাছে তারা অপরিচিত লোক মনে হলো। তারপর সে তার স্ত্রীর নিকটে চুপি চুপি গেল এবং একটা মোটা তাজা ভুনা বাছুর এনে (খাবার জন্যে) মেহমানদের সামনে রাখলো। তারপর বললো, তোমরা খাচ্ছ না কেন? (তাদেরকে খেতে না দেখে) তাদের সম্পর্কে সে মনে মনে ভয় পেয়ে গেল। তারা বললো, ভয় পেয়ো না; তারা তাকে এক জ্ঞানী পুত্রের সুসংবাদ দিল। এ কথা শুনে তার স্ত্রী চিৎকার করতে করতে সামনে এলো এবং আপন গাল চাপড়িয়ে বলতে লাগলো- এ বৃদ্ধা-বন্ধ্যার (ছেলে হবে)?
তারা বললো, তোমার রব তাই বলেছেন। তিনি বিজ্ঞ ও সবকিছু জানেন।
ইব্রাহীম বললো, হে খোদার প্রেরিত ফেরেশতাগণ, তোমরা কোন অভিযানে এসেছ?
তারা বললো, আমরা এক অপরাধী জাতির প্রতি প্রেরিত হয়েছি, যেন তাদের উপর পাকা মাটির পাথর বর্ষণ করি যা তোমার খোদার সীমালংঘনকারী লোকদের জন্যে চিহ্নিত আছে”- (যারিয়াতঃ ২৪-৩৪)।
কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে-
“আর আমরা লূতকে পাঠালাম, যখন সে তার জাতির লোককে বললো, তোমরা তো এমন নির্লজ্জ গর্হিত কাজ কর যা তোমাদের আগে দুনিয়ায় কেউ করেনি। তোমাদের অবস্থা কি এই যে, তোমরা (যৌনক্রিয়ার জন্যে) পুরুষদের কাছে যাও, রাহাজান কর এবং নিজেদের মজলিসে (সবার সামনে) খারাপ কাজ কর।
তার জাতির কাছে এ ছাড়া আর জবাব ছিল না- ‘নিয়ে এসো তোমার আল্লাহর আজাব যদি তুমি সত্যবাদী হয়ে থাক’।
লূত বললো, হে আমার খোদা! এসব দুষ্কৃতিকারী লোকদের মুকাবিলায় তুমি আমাকে সাহায্য কর।
তারপর আমার প্রেরিত ফেরেশতারা যখন সুসংবাদসহ ইব্রাহীমের কাছে পৌঁছলো, তখন তারা বললো, আমরা এ জনপদের লোকদেরকে ধ্বংস করে দেব। তারা বড়ো জালেম হয়ে পড়েছে।
ইব্রাহীম বললো, সেখানে তো লূতও আছে। তারা বললো, আমরা ভালোভাবে জানি সেখানে কে কে আছে। আমরা তাকে এবং তার স্ত্রী ছাড়া তার পরিবারের অন্যান্য লোকদেরকে রক্ষা করব। তার স্ত্রী পেছনে পড়ে থাকা লোকদের মধ্যে ছিল (এ জন্যে)। পরে আমার ফেরেশতারা যখন লূতের নিকট পৌঁছলো তখন তাদের আগমনে সে খুবই উদ্বিগ্ন ও মনমরা হয়ে পড়লো। তারা বললো, ভয় নেই, চিন্তা ও দুঃখ করো না, আমরা তোমাকে ও তোমার পরিবারের লোকদেরকে বাঁচাব- তোমার স্ত্রী ছাড়া, যে পেছনে পড়ে থাকা লোকদের মধ্যে গণ্য। আমরা এ লোকদের উপর আসমান থেকে আজাব নাযিল করব, সে সব পাপাচারের জন্যে যা তারা করে”- (আনকাবুতঃ ২৮-৩০)।
আল্লাহর ফেরেশতাগণ সুশ্রী ও সুদর্শন বালকের রূপ ধারণ করে হযরত লূতের মেহমান হয়েছিলেন। হযরত লূত (আ) বুঝতে পারেননি যে, তাঁরা ফেরেশতা ছিলেন। শহরের পাপিষ্ঠ লোকেরা সুন্দর সুন্দর বালকের আগমেন সংবাদের আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে পড়ে এবং হযরত লূতের বাড়ীতে ভিড় জমাতে থাকে। কুরআনে তার এভাবে বর্ণনা দেয়া হয়েছে-
“ইতোমধ্যে শহরবাসী আনন্দে গদগদ হয়ে লূতের বাড়িতে চড়াও হলো। লূত বললো, ভাইসব, এসব আমার মেহমান, আমার মুখ কালো করো না। আল্লাহকে ভয় কর, আমাকে লাঞ্ছিত করো না। তারা বললো, তোমাকে কি আমরা বার বার বারণ করে দেইনি যে, সারা দুনিয়ার ঠিকাদার হয়ো না? অবশেষে অতি প্রত্যুষে এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণ তাদেরকে পেয়ে বসলো। গোটা জনপদকে আমরা লণ্ডভণ্ড ও ওলট-পালট করে দিলাম। পোড়ামাটির পাথর তাদের উপর বর্ষণ করলাম”- (আল হিজরঃ ৬৭-৭৪)।
এমনও হতে পারে যে, একটি আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণে এসব প্রস্তর মাটির তলা থেকে উৎক্ষিপ্ত হয়ে জনপদ ধ্বংস করেছে। অথবা এমনও হতে পারে যে, প্রচণ্ড ঝড়-ঝঞ্ঝা প্রস্তর বর্ষণ করে।
হযরত লূতের কর্মক্ষেত্র
হযরত লূত (আ) ইব্রাহীম (আ)-এর ভাইপো ছিলেন। এমন অঞ্চল তাঁর কর্মক্ষেত্র ছিল যাকে আজকাল ট্রান্সজর্দান (Trans Jordan) বলে যা ইরাক ও ফিলিস্তিনের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। এ অঞ্চলের সদর ও কেন্দ্রীয় স্থানের নাম বাইবেলে সদোম (SODOM) বলা হয়েছে। যেহেতু সদোমবাসী লূত জাতি সমকামিতার পাপাচারে লিপ্ত ছিল, সেজন্যে বর্তমানকালেও পুরুষদের মধ্যে পরস্পর যৌনক্রিয়াকে sodomy বলা হয়। এ শহরটি লূত সাগরের (DEAD SEA) পার্শ্ববর্তী কোন স্থানে অবস্থিত ছিল যা সাগরে নিমজ্জিত হয়ে যায়।
যে ঘৃণ্য ও লজ্জাজনক দুষ্কর্মের জন্যে লূত জাতি কুখ্যাত হয়ে আছে, তা আজও চরিত্রহীন লোকেরা পরিত্যাগ করতে পারেনি। গ্রীক দার্শনিকরা এ জঘন্য অপরাধকে একটা নৈতিক গুণ বলে অভিহিত করে এবং জার্মানীসহ বিভিন্ন পাশ্চাত্য দেশে একে আইনসিদ্ধ করা হয়েছে। অতীত জাহেলিয়াতের যুগের যে ঘৃণ্য অপরাধকে মানুষ অপরাধ মনে করেনি, বর্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতা তথা আধুনিক জাহেলিয়াতের যুগে এ কাজকে ন্যায়সঙ্গত বলে প্রচার করা হচ্ছে।
সমমৈথুন একটি প্রকৃতি-বিরোধী কাজ। মানুষ ব্যতীত অন্য কোন প্রাণীর মধ্যে সমমৈথুন দেখতে পাওয়া যায় না। মানুষকে পরীক্ষা করার জন্যে কর্মস্বাধীনতা দান করা হয়েছে। মানুষ এ স্বাধীনতার অপব্যবহার করে প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছে।
আল্লাহতায়ালা সমস্ত জীবজন্তুর মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষের পার্থক্য করে রেখেছেন বংশবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে। মানুষের বেলায় এর পশ্চাতে অতিরিক্ত এক মহান উদ্দেশ্য রয়েছে তা এই যে, স্বামী-স্ত্রী মিলে একটি পরিবার গঠন করবে এবং তার থেকে গড়ে উঠবে সমাজ ও সভ্যতা। এ উদ্দেশ্যে উভয়ের লিংগ ভিন্ন ধরনের করা হয়েছে। তাদের আকার-আকৃতি, গঠন, আপন-আপন কর্মক্ষমতা ও কর্মধারাও পৃথক করা হয়েছে। একটিকে কর্মক্ষমতা দান করা হয়েছে এবং অপরটিকে সে কর্মের প্রভাব গ্রহণের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। তাদের পারস্পরিক মিলন ও সংগমে রেখে দেয়া হয়েছে এক অপূর্ব স্বাদ আস্বাদন যা পরস্পরকে আকৃষ্ট করে। যে মানুষ (মানুষ ব্যতীত অন্য কোন প্রাণী এ কাজ করে না) প্রকৃতি পরিপন্থী সমমৈথুনের মাধ্যমে যৌন লালসা চরিতার্থ করে, সে একই সাথে কয়েক প্রকারের অপরাধ করে।
এক- সে নিজেই তার ক্রিয়াকর্মের ধরন ও গঠন এবং মনস্তাত্ত্বিক প্রকৃতির সাথে সংগ্রাম করে এবং এতে এক চরম বিকৃতি ও বিপর্যয়ের সৃষ্টি করে, যার ফলে তার দেহ, মন ও নৈতিকতার উপর বিরাট প্রভাব পড়ে।
দুই- সে প্রকৃতির সাথে চরম বিশ্বাসঘাতকতা করে। কারণ যে যৌন আনন্দ আস্বাদনকে সমাজ-সভ্যতার খেদমতের পারিশ্রমিক গণ্য করা হয়েছে এবং যে পারিশ্রমিক লাভের জন্যে কিছু দায়িত্ব-কর্তব্য আরোপ করা হয়েছে, তা সে লাভ করতে চায় কোন প্রকার দায়িত্ব-কর্তব্য পালন না করেই।
তিন- সে সমাজের সাথেও বিশ্বাসঘাতকতা করে। সে সমাজে প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন তামাদ্দুনিক প্রতিষ্ঠানের ফায়দা হাসিল করে। কিন্তু নিজে এ সবের কোন খেদমত না করে একান্ত স্বার্থপরতার সাথে তার দৈহিক শক্তি ও সময় এমন কাজে ব্যয় করে- যা সমাজ সভ্যতা ও নৈতিকতার জন্যে ভয়ানক ক্ষতিকর হয়। সে নিজেকে তার বংশ-পরিবারের খেদমতের একেবারে অযোগ্য বানিয়ে দেয়। সে নিজের সাথে অন্ততঃ একজন পুরুষকে অস্বাভাবিক নারীসুলভ কাজে নিয়োজিত করে এবং অন্ততঃ দু’জন নারীর জন্যে যৌন উৎশৃংখলতা, নৈতিক অধঃপতন ও বিপর্যয়ের দুয়ার খুলে দেয়। এ কারণেই লূত জাতিকে আল্লাহ তায়ালা দুনিয়ার বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেন, যাতে করে বিবেকবান মানুষ এ থেকে শিক্ষাগ্রহণ করতে পারে।
শুয়াইব জাতি
মাদইয়ানবাসী এবং আয়কাহবাসীকে শুয়াইব জাতি নামে অভিহিত করা হয়েছে। তাদের হেদায়েতের জন্যে আল্লাহতায়ালা হযরত শুয়াইব (আ)-কে নবী করে পাঠান। এ সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে যে, মাদইয়ানবাসী ও আয়কাহবাসী কি একই জাতি ছিল, না পৃথক পৃথক দু’টি জাতি। কেউ কেউ এ দু’টিকে দু’টি পৃথক জাতি বলেছেন। কেউ কেউ উভয়কে একই জাতি বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। অনুসন্ধানে জানতে পারা যায় যে, উভয় মতই সঠিক। মাদইয়ানবাসী ও আয়কাহবাসী দু’টি পৃথক জাতি হলেও তারা একই বংশের দু’টি শাখা। হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর যেসব সন্তান তাঁর বিবি কাতুরার গর্ভজাত তারা বনী কাতুরা নামে খ্যাত। তাদের মধ্যে যে গোত্রটি সবচেয়ে বেশি প্রসিদ্ধ তা মাদইয়ান বিন ইব্রাহীমের দিক দিয়ে ‘আসহাবে মাদইয়ান’ নামে খ্যাত। তাদের আবাসস্থল উত্তর হেজাজ থেকে শুরু করে, ফিলিস্তিনের দক্ষিণাঞ্চল এবং সেখান থেকে সিনাই উপত্যকার শেষপ্রান্ত পর্যন্ত লোহিত সাগর ও আকাবা উপসাগরের তীর পর্যন্ত বিস্তৃত। তার সদর কেন্দ্রীয় স্থল মাদইয়ান শহর। বনী কাতুরার অবশিষ্ট গোত্রগুলোর মধ্যে দেদান (Dedanites) তুলনামূলকভাবে অধিক প্রসিদ্ধ। তারা উত্তর আরবের তাইমার এবং তবুক ও আলউলার মধ্যবর্তী অঞ্চলে বসবাস করে। তাদের কেন্দ্রীয় শহর ছিল তবুক, যাকে প্রাচীনকালে আয়কাহ বলা হতো। মাদইয়ানবাসী ও আয়কাহবাসীদের জন্যে একই পয়গম্বর পাঠাবার কারণ সম্ভবতঃ এ ছিল যে, উভয়ে একই বংশোদ্ভূত ছিল এবং একই ভাষায় কথা বলতো। উভয়ের অঞ্চল পরস্পর সংলগ্ন ছিল। তাদের মধ্যে হয়তো বিয়ে-শাদীরও প্রচলন ছিল এবং উভয়ের পেশা ছিল ব্যবসায়-বাণিজ্য। তাদের নৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থা একই রকম। তারা ব্যবসায়ে ছিল অত্যন্ত দুর্নীতিপরায়ণ। শির্ক-কুফরেও তারা নিমজ্জিত ছিল।
“আর মাদইয়ানবাসীদের প্রতি আমরা তাদের ভাই শুয়াইবকে পাঠালাম। সে বললো, হে আমার জাতির লোকেরা! আল্লাহর দাসত্ব-আনুগত্য কর। তিনি ছাড়া তোমাদের খোদা কেউ নেই। আর ওজন ও মাপ-জোকে কম করো না। আজ তোমাদেরকে আমি ভালো অবস্থায় দেখছি। কিন্তু আমার ভয় হয়, কাল তোমাদের উপর এমন দিন আসবে যার আজাব তোমাদের সকলকে ঘিরে ফেলবে। হে আমার জাতির ভাইয়েরা! ঠিক ঠিকভাবে ইনসাফ সহকারে পূর্ণ ওজন ও পরিমাপ কর। আর লোকদের জিনিসে (ভেজাল বা খারাপ মাল দিয়ে) কোনরূপ ক্ষতির সৃষ্টি করো না। আর দুনিয়ায় ফাসাদ ছড়িয়ে বেড়িয়ো না”- (হুদঃ ৮৪-৮৫)।
পূর্ববর্তী নবীর শিক্ষা-দীক্ষা ভুলে যাওয়ার ফলে তারা প্রকৃতির দাস হয়ে পড়েছিল। খোদার পরিবর্তে তারা মনগড়া দেবদেবীর পূজা করতো। তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতকে তারা অস্বীকার করতো। ফলে তারা হয়ে পড়েছিল দুর্নীতিপরায়ণ, জালেম ও পাপাচারী। লূত জাতির ন্যায় বিশ্বাসমূলক গোমরাহির সাথে সাথে নৈতিক অবক্ষয়, ব্যবসায়ে অসাধুতা ও দুর্নীতিতে তারা কুখ্যাত হয়ে পড়েছিল। শুয়াইব নবী তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে চারিত্রিক সংশোধনের জন্যে নামাযের তাগিদও করেন। তারা তা কিছুতেই মানতে রাজি ছিল না।
শুয়াইবের জাতির লোকেরা জবাবে বলে-
“হে শুয়াইব! তোমার এ নামায কি (আমাদের প্রতি এ দাবি করার) হুকুম দিচ্ছে যে, আমরা ঐসব খোদা পরিত্যাগ করব আমাদের পূর্বপুরুষ যাদের পূজা করতো?”- (হুদঃ ৮৭)।
‘আমাদের পূর্বপুরুষ যাদের পূজা করতো’- কথাটির মধ্যে জাহেলিয়াতের সেই অন্ধ অনুসরণ নীতির এক খোঁড়া যুক্তি লুকায়িত আছে। তাদের কথা হলোঃ আমাদের জ্ঞানী গুণী মনীষীদের তুলনায় তোমার কথার কি মূল্য আছে? তাঁরা যে অমুক অমুককে খোদা বলে মানতেন- তা ভুল ছিল, আর তোমার কথাই ঠিক?
তাঁর নবুওতের দাবির প্রতি উপহাস করে বললো, তুমি আল্লাহর প্রেরিত এ কথা মিথ্যা। আমাদের মতই একজন মানুষ হয়ে তুমি বিশ্বপ্রভুর প্রেরিত কি করে হতে পার? তুমি তো একটি পাগল। যাদু করে তোমার বুদ্ধি-বিবেক বিকল ও বিকৃত করা হয়েছে।
“তুমি একজন যাদুগ্রস্ত লোক। আর আমাদের মতো একজন মানুষ ছাড়া কিছু নও। আমরা তো তোমাকে মিথ্যাবাদীই মনে করি”- (শুয়ারাঃ ১৮৬)।
দাওয়াতের বুনিয়াদী দফা তারা যেভাবে প্রত্যাখ্যান করে, যেসব আজেবাজে যুক্তি পেশ করে তার মধ্যে নতুনত্ব কিছু ছিল না। পূর্ববর্তী নবীগণের দাওয়াত জাহেলিয়াত ও প্রবৃত্তির দাসগণ যেভাবে এবং যেসব খোঁড়া ওজর-আপত্তি তুলে প্রত্যাখ্যান করে, শুয়াইব জাতিও তাই করে। নবী শুয়াইব (আ) যখন তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যে দুর্নীতি, প্রতারণা ও বেঈমানীর তীব্র সমালোচনা করেন, তখন জাহেলিয়াতের এক নতুন দৃষ্টিভংগী প্রকাশ লাভ করলো। তাদের যুক্তি হলো যে, রুজি-রোজগারের সাথে নৈতিকতার কি সম্পর্ক? তারা নবীর মুখের উপর বলে দিলঃ তোমার এ মূর্খতাসুলভ কথায় আমরা আমাদের অর্থনৈতিক স্বার্থ কুরবানী করব? পরিমাপে হেরফের করে আমরা ব্যবসায়ে যে সুযোগ-সুবিধা লাভ করি তা এজন্যে পরিত্যাগ করব যে, আখিরাতে আমাদের ক্ষতি হবে? আর সেই আখিরাতটাই বা কি তা তো আমাদের বুঝে আসে না? আর যদি কখনো সংঘটিত হয়ও, তার জন্যে আমরা আমাদের দুনিয়া বরবাদ করব? নগদ ছেড়ে বাকীর আশায় থাকা আমরা চরম বোকামি মনে করি। তোমার যা ভালো লাগে কর। আমাদের উপর তা চাপিয়ে দিচ্ছ কেন?
জাতির সমাজপতিরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে একে অপরকে সাবধান করে দিল।
“যেসব সর্দারেরা তাঁর কথা মানতে অস্বীকার করেছিল তারা পরস্পর বলাবলি করতে লাগলোঃ তোমরা যদি শুয়াইবের কথা মেনে চল তাহলে (আর্থিক দিক দিয়ে) বরবাদ হয়ে যাবে”- (আ’রাফঃ ৯০)।
এ সামান্য কথাটির তাৎপর্য অনেক বেশি। মাদইয়ানের সমাজপতি ও নেতৃবৃন্দের বক্তব্য ছিল এই যে, হযরত শুয়াইব (আ) যেসব কথা বলছেন, যে ঈমানদারী ও সততার দাওয়াত দিচ্ছেন এবং যেসব স্থায়ী নীতি-নৈতিকতার বন্ধনে আবদ্ধ করতে চাইছেন, তা আমরা কি করে মেনে নিতে পারি? আমরা দুনিয়ার সর্ববৃহৎ দু’টি বাণিজ্যিক রাজপথ নিয়ন্ত্রণ করে থাকি। আমরা মিসর ও ইরাকের মতো দু’টি উন্নত রাষ্ট্রের সীমান্তের উপরে বসবাস করি। আমরা যদি বাণিজ্যিক কাফেলাগুলির উপর আমাদের প্রভাব ও চাপ সৃষ্টি না করি এবং সৎ ও ভালো মানুষের মতো আচরণ করি, তাহলে আমাদের ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে আমরা যেসব সুযোগ-সুবিধা লাভ করছি তা সব নষ্ট হয়ে যাবে। তারপর পার্শ্ববর্তী জাতিগুলির উপর আমাদের যে প্রভাব-প্রতিপত্তি আছে তাও শেষ হয়ে যাবে।
দুনিয়াবী স্বার্থহানির এ আশংকা শুধু শুয়াইব জাতির সমাজপতিদের মধ্যেই সীমিত ছিল না, প্রত্যেক যুগের বিকৃত মন-মানসিকতা ও চরিত্রের লোকেরাই সততা ও বিশ্বস্ততার আচরণে এ আশংকাই অনুভব করেছে। প্রত্যেক যুগের বিপর্যয় সৃষ্টিকারী লোকদের এ ধারণাই ছিল যে, ব্যবসায়-বাণিজ্য, রাজনীতি এবং অন্যান্য পার্থিব কাজ-কারবার মিথ্যা, বেঈমানী এবং শঠতা-প্রতারণা ব্যতীত চলতে পারে না। প্রত্যেক যুগে ও স্থানে দাওয়াতে হকের মুকাবিলায় যেসব ভয়ানক ওজর-আপত্তি পেশ করা হয়েছে তার মধ্যে একটা এও ছিল যে, দুনিয়ার প্রচলিত পথ ও পন্থা পরিহার করে এ দাওয়াত মেনে নিলে জাতির ধ্বংস অনিবার্য। বর্তমান যুগের জাহেলিয়াতপন্থীরাও ঐ একই ধারণা পোষণ করে।
মাদইয়ানবাসী শুধু নবীর দাওয়াত অস্বীকারই করেনি, তাঁকে ও তাঁর অনুসারীদেরকে দেশ থেকে বহিষ্কার করার ধমকও দিয়েছে।
“গর্ব অহংকার মদমত্ত তাঁর জাতির সর্দার সমাজপতিরা বললো, হে শুয়াইব! তোমাকে এবং তোমার সাথে যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে আমাদের জনপদ থেকে অবশ্য অবশ্যই বের করে দেব, অন্যথায় তোমাদেরকে আমাদের মিল্লাতে ফিরে আসতে হবে”- (আ’রাফঃ ৮৮)।
যখন তাদের সৎপথে ফিরে আসার আর কোন সম্ভাবনাই রইলো না, তখন আল্লাহতায়ালা তাদেরকে ধ্বংস করে দিলেন।
“তারপর হলো এই যে, এক প্রলয়ংকরী দুর্যোগ তাদের উপর এসে পড়লো। তারপর তারা তাদের আপন আপন গৃহে উপুড় হয়ে মরে পড়ে রইলো”- (আ’রাফঃ ৯১)।
তাদের এ ধ্বংসকে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে-
“শুয়াইবের দাওয়াতকে মিথ্যা মনে করে যারা প্রত্যাখ্যান করেছিল, (তারা এমনভাবে নিশ্চিহ্ন হলো যে) যেন তারা কোনদিন এসব স্থানে মোটেই বসবাসই করেনি”- (আ’রাফঃ ৯২)।
মাদইয়ানবাসীর এ ধ্বংসলীলা বহুকাল যাবত পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের লোকদের জন্যে স্মরণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে রইলো। বাতিলপন্থীদের ধ্বংস এভাবেই হয়ে থাকে।
ফেরাউনের জাতি
কালের চাকা ঘুরতেই থাকে এবং ইসলাম ও জাহেলিয়াতের দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষও চলতেই থাকে। অবশেষে এক সময় মিসর ভূখণ্ডে আল্লাহর প্রিয় নবী হযরত ইউসুফ (আ)-এর তিরোধানের কয়েকশ’ বছর পর কিবতী জাতি উন্নতির উচ্চশিখরে আরোহণ করে এবং ফেরাউনী পরিবারের শাসন কায়েম হয়। ফেরাউনী শাসনকালে গোটা জাতি জাহেলিয়াতের অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। ইসলামের প্রতি বিশ্বাস পোষণকারী বনী ইসরাইলের প্রতি চরম নির্যাতন-নিষ্পেষণ শুরু হয়। কিবতীদের ভ্রান্ত সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রভাবে বনী ইসরাইলগণও বিকৃতির শিকার হয়। তাদের সংস্কার, সংশোধন ও পথনির্দেশনা এবং ফেরাউনী শাসনের অক্টোপাস থেকে তাদের মুক্তির উদ্দেশ্যে যখন হযরত মুসাকে (আ) সে দেশে প্রেরণ করা হয়, তখন কিবতী জাতির মধ্যেও ইসলামী দাওয়াতের দায়িত্ব তাঁর উপর অর্পিত হয়। নবীগণের দাওয়াতের রীতিনীতি অনুযায়ী হযরত মুসা (আ) জাতির শাসক হিসেবে ফেরাউন ও তার সভাসদবৃন্দকে তাঁর দাওয়াতের প্রথম টার্গেট (লক্ষ্য) হিসেবে বেছে নেন। আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর প্রতি সে নির্দেশই দেয়া হয়।
“ফেরাউনের কাছে যাও। সে বিদ্রোহী হয়েছে। তাকে গিয়ে বলঃ তুমি কি এজন্যে প্রস্তুত যে, পবিত্রতা অবলম্বন করবে এবং আমি তোমার রবের দিকে তোমাকে পথ দেখাই যাতে তোমার মধ্যে তাঁর ভয় সৃষ্টি হয়”- (নাযিয়াতঃ ১৭-১৯)।
“জালেম জাতির কাছে যাও- ফেরাউন জাতির কাছে, এরা কি ভয়াবহ পরিণাম থেকে বাঁচতে চায় না?”- (শুয়ারাঃ ১১)।
কুরআন পাকের বহু স্থানে প্রসংগক্রমে হযরত মুসা (আ) ও ফেরাউনের উল্লেখ করা হয়েছে। তা একত্র করলে এক দীর্ঘ ইতিহাস হবে। সে ধারাবাহিক ইতিহাস বর্ণনা করার পরিবর্তে এখানে জাহেলিয়াতের চিরাচরিত কূটতর্ক, হঠকারিতা, অন্ধ অনুসরণ ও কুসংস্কারের মৌলিক দিকগুলি তুলে ধরা হচ্ছে। প্রথমে তাদের কুসংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাসের কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হলো।
ফেরাউন নামের অর্থ
ফেরাউন শব্দের অর্থ সূর্যদেবতার সন্তান। প্রাচীন মিসরবাসীর মহাদেবতা ছিল সূর্য এবং সূর্যকে তারা রা’ বলতো। ফেরাউন বলতে তার সন্তানদেরকেই বুঝাতো। মিসরবাসী বিশ্বাস করতো যে, দেশ শাসনের ক্ষমতা সেই পেতে পারে যে রা’ দেবতার রূপ ধারণ করে তার অবতার হিসেবে আগমন করবে। এ বিশ্বাস অনুযায়ী মিসরে যে রাজবংশই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তাদেরকে সূর্যদেবতার বংশধর বলে প্রচার করা হতো। যে ব্যক্তিই শাসন ক্ষমতার আসনে সমাসীন হতো সে নিজেকে ফেরাউন নামে অভিহিত করতো। আসলে এটা প্রকৃত নাম নয়, একটি রাজউপাধি মাত্র। এর থেকে এ ধারণাও দেয়া হতো যে, যেহেতু সে দেবতার অবতার, অতএব সে সেই দেশবাসীর পরমেশ্বর বা মহাদেবতা।
উল্লেখ্য যে, হযরত মুসা (আ)-এর কাহিনী বর্ণনা প্রসঙ্গে কুরআন পাকে দু’জন ফেরাউনের উল্লেখ পাওয়া যায়। একজন যার শাসনকালে হযরত মুসা (আ) জন্মগ্রহণ করেন এবং তার দ্বারা লালিত-পালিত হন। গবেষকদের মতানুসারে তার নাম ছিল দ্বিতীয় আমীস। যার নিকটে ইসলামের দাওয়াত ও বনী ইসরাইলের মুক্তির দাবিসহ হযরত মুসা (আ) প্রেরিত হয়েছিলেন- সে ছিল দ্বিতীয় ফেরাউন, নাম ‘মুনফাতা’ বা ‘মিনফাতা’।
ফেরাউনের জাতিকে আল্লাহতায়ালা স্বয়ং জালেম জাতি বলে অভিহিত করেন। গোটা জাতি জালেম এবং ফেরাউন সে জালেমদের সর্দার ছিল। এতে করে তার অত্যাচার, নির্যাতন যে কত নিষ্ঠুর, পৈশাচিক ও লোমহর্ষক ছিল তা অনুমান করা যায়। তাই ইসলামী দাওয়াতের জবাবে তারা পূর্বের খোদাদ্রোহীদের মতোই আচরণ করেছিল। তারা বলেছিল-
“এসব কথা তো আমাদের বাপ-দাদার আমলে কখনোই শুনিনি”- (কাসাসঃ ৩৬)।
নবীর দাওয়াত অস্বীকার করার পেছনে যুক্তি ঐ একই ছিল। অর্থাৎ পূর্বপুরুষদের অন্ধ অনুসরণ। তাদের মূলকথাঃ আমাদের পূর্বপুরুষ অবশ্যই জ্ঞানী-গুণী ছিলেন, তারা যখন খোদাকে এক ও লা-শরীক মানতেন না, আখিরাতেরও কোন ধারণা পোষণ করতেন না, আর না এ ধারণা রাখতেন যে, সাধারণ এক মানুষ খোদার প্রেরিত হতে পারে, তাহলে এ ব্যক্তির কথা কি করে বিশ্বাস করা যায়?
সকল যুগের এ ধরনের মানসিকতা সম্পর্কে কুরআনে পরিষ্কার ভাষায় বলা হয়েছে-
“তাদেরকে যখন বলা হয় যে, আল্লাহ যেসব হুকুম নাযিল করেছেন তা মেনে চল, তখন তারা জবাবে বলে, আমরাও সেসব রীতিনীতিই মেনে চলব যেসব মেনে চলতে আমরা আমাদের বাপদাদাকে দেখেছি।”
“আচ্ছা যদি তাদের বাপদাদা বুদ্ধি-বিবেচনাসহ কোন কাজ করে না থাকে এবং সরল-সঠিক পথের সন্ধান পেয়ে না থাকে, তাহলেও কি এরা তাদের অনুসরণ করতে থাকবে?”- (বাকারাহঃ ১৭০)।
“আল্লাহর পথে চলতে অস্বীকার যারা করেছে তাদের অবস্থা ঠিক এরূপ, যেমন রাখাল পশুগুলিকে ডাকে, কিন্তু তারা ঐ ডাকের আওয়াজ ব্যতীত আর কিছুই শুনতে পায় না। এরা বধির, বোবা, অন্ধ। এ জন্যে কোন কথা এরা বুঝতে পারে না”- (বাকারাহঃ ১৭১)।
খোদা ও আখিরাতের ভয়, সৎকর্মশীলতা, মহান চারিত্রিক গুণাবলীর ধারণা সুস্থ বিবেকেরই কামনার বস্তু। এতে আত্মার পরম প্রশান্তি লাভ করা যায়। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা প্রত্যাখ্যান করে। এ নির্বুদ্ধিতাসুলভ আচরণের কারণ সকল যুগে একই ধরনের হয়ে থাকে। মানুষের আত্মবিস্মৃতি, মন মানসিকতা ও চিন্তাচেতনার বিস্মৃতি, প্রবৃত্তিপূজা, পূর্বপুরুষদের অন্ধ অনুকরণপ্রিয়তা, ক্ষমতামদমত্ত গর্ব অহংকার প্রভৃতি এমন কঠিন যবনিকা বা লৌহ প্রাচীরের মত কাজ করে যে, তা অতিক্রম করে হেদায়েতের আলো মানুষের হৃদয় প্রদেশে প্রবেশ করতে পারে না। তাই তাদেরকে বধির, বোবা ও অন্ধের সাথে তুলনা করা হয়েছে।
সকল যুগে, কি অতীত যুগে আর কি আধুনিক যুগে, একই অবস্থা দেখতে পাওয়া যায়। ফেরাউন ও তার পারিষদবর্গের মধ্যে তা-ই দেখা গেছে। ক্ষমতামদমত্ত ফেরাউন আল্লাহতায়ালার একত্ব, প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব, সার্বভৌমত্ব, সৃষ্টিজগতের উপর একচ্ছত্র আধিপত্য সবকিছুই অস্বীকার করে বসে। হযরত মুসা (আ) এবং তাঁর ভাই হযরত হারুন (আ) খোদার নির্দেশে ফেরাউনের মন্ত্রীসভার বৈঠকে সকলের সামনে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেন-
“নিঃসন্দেহে আমরা রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে প্রেরিত”- (শুয়ারাঃ ১৬)।
“তারা সাথে সাথেই বলে ওঠে, এ রাব্বুল আলামীন আবার কোন জিনিস?”- (শুয়ারাঃ ২৩)।
তাদের এ জিজ্ঞাসার মধ্যে বিস্ময় ছিল এবং কিছুটা বিদ্রুপও ছিল। তার অর্থ এ ছিল না যে, তারা একেবারে নাস্তিক ছিল, খোদার অস্তিত্ব অস্বীকারকারী ছিল। বরং বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ এমনকি তাঁর ফেরেশতাদের অস্তিত্বেও তারা বিশ্বাসী ছিল।
“একদিন ফেরাউন তার জাতির লোকদেরকে ডেকে বললোঃ হে জাতির লোকেরা! মিসরের বাদশাহী কি আমার নয়? আর এ নদ-নদীগুলি কি আমার অধীনে প্রবাহিত নয়? তোমরা কি তা দেখছ না? আমি কি ভালো মানুষ, না এ ব্যক্তি যে হীন ও লাঞ্ছিত? সে নিজের কথাও স্পষ্ট করে বলতে পারে না। তার উপর সোনার কাঁকন ফেলে দেয়া হয়নি কেন? অথবা (আল্লাহর প্রেরিত হলে) ফেরেশতাদের একটা বাহিনী তার আগে-পিছে পাহারাদারীর জন্যে এলো না কেন?”- (যুখরুফঃ ৫১-৫৩)।
তার ভ্রান্ত সংকীর্ণ চিন্তাধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গি এই ছিল যে, আল্লাহ বিশ্বজগতের স্রষ্টা এবং বিরাট বিশাল প্রকৃতিরাজ্যে তাঁর কর্তৃত্ব ও হুকুম শাসন চলছে, চলুক। কিন্তু মিসর ভূখণ্ডের বাদশাহ যেহেতু আমি এবং এ দেশের পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী, গাছপালা, মানুষ ও জীবকুলের মালিক যেহেতু আমি, অতএব আমার দেশে আমার হুকুম শাসন ছাড়া আর কারো হুকুম শাসন চলতে পারে না। সে ছিল অত্যন্ত ক্ষমতা গর্বিত। যার ফলে সে গোটা জাতিকে তার অনুগত দাসানুদাসই মনে করতো। সে সকলকে তুচ্ছ, নগণ্য ও ঘৃণ্য লাঞ্ছিত মনে করতো। তার ক্ষমতা-দাপট ও গর্ব-অহংকার হযরত মুসার (আ) নবুওত মেনে নিতে দেয়নি। তাছাড়া তার দৃঢ় বিশ্বাস, মানুষ কখনো আল্লাহর প্রেরিত রসূল হতে পারে না। আর আল্লাহর কাউকে রসূল করার ইচ্ছা থাকলে সমাজে যে ধন-ঐশ্বর্য ও ক্ষমতার অধিকারী তাকেই রসূল বানানো মানায়। হযরত মুসা (আ) সমাজে প্রতিষ্ঠিত প্রভাব-প্রতিপত্তিশীল ও ধনশালী কোন ব্যক্তি নয়, তার হাতে সোনার কাঁকনও নেই এবং আল্লাহর প্রেরিত প্রতিনিধি হলে অবশ্যই সামনে এবং পেছনে ফেরেশতাদের বিরাত বাহিনী থাকতো, রাজা বাদশাহদের মতো সে শান-শওকতসহ চলাফেরা করতো। এর কোনটিই যখন নেই, তখন তার সকল দাবি মিথ্যা।
বহু অকাট্য যুক্তি, সুস্পষ্ট নিদর্শনাদি ও অলৌকিক ক্রিয়াকর্ম প্রদর্শনের পরও সে তার অন্ধ জিদ, ঔদ্ধত্য ও হঠকারিতা থেকে বিরত না হয়ে আল্লাহর নবীর প্রতি কঠোরতর হতে থাকে। সে মুসাকে (আ) কঠোর ধমকের স্বরে বলে-
“ফেরাউন বললো, তুমি যদি আমি ছাড়া আর কাউকে খোদা মেনে নাও, তাহলে তুমি তাদের মধ্যে শামিল হবে যারা জেলের অন্ধকার কুঠরিতে ধুঁকে ধুঁকে মরছে”- (শুয়ারাঃ ২৯)।
“আমরা মুসাকে ফেরাউন, হামান ও কারুনের কাছে আমাদের নিদর্শনাবলী এবং নবী হিসেবে নিয়োগের সুস্পষ্ট সনদসহ পাঠালাম। কিন্তু তারা বললো, সে যাদুকর, মিথ্যাবাদী। তারপর যখন সে আমাদের পক্ষ থেকে সত্য তাদের সামনে নিয়ে এলো, তারা বললো- তাকে হত্যা কর এবং তারা সাথে যারা ঈমান এনেছে তাদের সন্তানদেরকেও। আর মেয়েদেরকে জীবিত ছেড়ে দাও। কিন্তু তাদের কূটকৌশল ব্যর্থ হলো। এবং ফেরাউন বললো, আমাকে ছেড়ে দাও, তাকে আমি হত্যা করছি। সে তার রবকে ডাকুক। আমার ভয় হচ্ছে যে সে তোমাদের দ্বীন বদলে দেবে অথবা দেশে ফাসাদ সৃষ্টি করবে। মুসা বললোঃ আমি প্রত্যেক গর্বিত অহংকারীর মুকাবিলায়- যে হিসেবের দিনের প্রতি ঈমান রাখে না- আমার এবং তোমাদের রবের আশ্রয় নিয়েছি”- (মুমেনঃ ২৩-২৭)।
অর্থাৎ মানুষের সকল প্রকার আনুগত্য-গোলামীর শৃঙ্খল ছিন্ন করে একমাত্র আল্লাহর গোলামী বা হুকুম-শাসনের অধীন হওয়াই ছিল নবীগণের দাওয়াতের লক্ষ্য। ফেরাউন-নমরুদের মতো সকল যুগের স্বৈরাচারী শাসক তাদের দেশের সকল মানুষের একচ্ছত্র প্রভু হয়ে থাকতে চায়। সকলের উপর তাদেরই হুকুম শাসন চলবে, জনগণ যেন তাদেরই আইনের অধীন হয়ে থাকে। হযরত মুসার (আ) ইসলামী দাওয়াতের ফলে ফেরাউনের এ আশংকাই হয়েছিল যে, তার একচ্ছত্র প্রভুত্ব-আধিপত্য আর চলবে না। মুসার দাওয়াত মানুষের মধ্যে এমন এক মানসিক বিপ্লব এনে দেবে যে, তারা মানুষের গোলামি থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করবে। এ আশংকা পোষণ করেই ফেরাউন তার সভাসদদের কাছে বললো, মুসার দ্বারা এক বিপ্লবের আশংকা আমি করছি। বিপ্লব করতে না পারলেও নিদেনপক্ষে এ আশংকা তো অবশ্যই আছে যে, তার প্রচার-প্রচারণায় দেশে বিশৃংখলা-অরাজকতা সৃষ্টি হবে, মানুষের শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে। অতএব হত্যার অপরাধী না হলেও নিছক জননিরাপত্তার (Maintenance of Public Order) খাতিরে তাকে হত্যা করা উচিত।
ফেরাউন বিপ্লব এ অর্থে বলেছে যে, প্রচলিত দ্বীন মুসা (আ) পরিবর্তন করে দেবেন।
“আমার ভয় হয় যে, সে তোমাদের দ্বীন বদলে দেবে।”
দ্বীন বলতে এখানে বুঝানো হয়েছে শাসন ব্যবস্থা। ফেরাউন ও তার পরিবারের সার্বভৌমত্বের ভিত্তিতে ধর্ম, রাজনীতি, অর্থনীতি ও সংস্কৃতির যে ব্যবস্থা মিসরে চলছিল তা-ই ছিল সে দেশের ‘দ্বীন’। হযরত মুসার (আ) দাওয়াতের ফলে তাদের এ দ্বীন পরিবর্তনের আশংকা দেখা দিয়েছিল, তার নিজের বাদশাহী, তার প্রভুত্ব-কর্তৃত্ব খতম হয়ে যাবে। অতএব দ্বীন পরিবর্তনকারীকে হত্যা অবশ্যই করতে হবে। প্রত্যেক যুগেই এমনকি আধুনিক যুগের স্বৈরাচারী ফেরাউনরা যখন উপলব্ধি করেছে যে, ইসলামী আন্দোলন তাদের স্বৈরশাসনের ভিত প্রকম্পিত করে দিয়েছে, তখন হয় আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা ও বানোয়াট অভিযোগ খাড়া করতঃ বিচারের প্রহসন করে আন্দোলনের নেতৃবৃন্দকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছে, অনেককে কারাদণ্ড দেয়া হয়েছে এবং অনেকের উপরে পৈশাচিক নির্যাতন চালানো হয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত খোদাদ্রোহী স্বৈরাচারী শক্তিই ধ্বংস হয়েছে। ফেরাউন তার সমস্ত রাষ্ট্রশক্তি ব্যবহার করেও হযরত মুসা (আ), তাঁর ইসলামী আন্দোলন ও শক্তিকে নির্মূল করতে পারেনি। স্বয়ং সে ধরাপৃষ্ঠ থেকে নির্মূল ও নিশ্চিহ্ন হয়েছে।
ফেরাউন যখন হযরত মুসাকে (আ) হত্যা করার সকল প্রস্তুতি গ্রহণ করলো, তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর প্রতি নির্দেশ এলো সমগ্র ইসলামী জনশক্তি নিয়ে মিসর ভূখণ্ড থেকে বেরিয়ে পড়ার।
“রাতের মধ্যেই তুমি আমার বান্দাহদের নিয়ে বেরিয়ে পড়। তোমাদেরকে কিন্তু ধাওয়া করা হবে। সমুদ্রকে তার নিজের (প্রবহমান) অবস্থায় ছেড়ে দিও। এ সমগ্র বাহিনী নিমজ্জিত হয়ে মরবে। কত বাগবাগিচা, ঝর্ণাধারা, ক্ষেতখামার ও আলীশান রাজপ্রাসাদ তারা পেছনে ফেলে গিয়েছিল। কতই না বিলাস সামগ্রী যা তারা উপভোগ করছিল, পেছনে পড়ে রইলো। এ হলো তাদের পরিণাম এবং আমরা অন্য লোকদেরকে এসবের উত্তরাধিকারী বানালাম। তারপর না আসমান, না যমীন তাদের জন্য অশ্রু বিসর্জন করলো এবং তাদেরকে কিছুমাত্র অবকাশও দেয়া হলো না”- (দুখানঃ ২৩-২৯)।
হযরত মুসা (আ) আল্লাহতায়ালার নির্দেশে লোহিত সাগরের উপর তাঁর অলৌকিক লাঠি দ্বারা আঘাত করা মাত্র এপার-ওপার একটি সুন্দর ও শুকনো রাজপথ তৈরি হয়ে যায়। গোটা ইসলামী জনশক্তি নিরাপদে সমুদ্র পার হয়ে যায়। অতঃপর ফেরাউন তার বিরাট বাহিনীসহ রাজপথ দিয়ে চলা শুরু করলে হঠাৎ সমুদ্র তার স্বাভাবিক রূপ ধারণ করে এবং সমগ্র বাহিনী সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়ে প্রাণ হারায়। এ ধরনের স্বৈরাচারী শাসকদের যতোই বিজয়ডংকা বাজুক না কেন, এবং চাটুকার দল তাদের প্রশংসায় যতোই পঞ্চমুখ হোক না কেন, তাদের মৃত্যুর পর কেউ তাদের জন্যে শোক প্রকাশ করে চোখের পানি ফেলে না। বরং সকলেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে।
ইতিহাসের প্রতিটি অধ্যায়ে আমরা ইসলাম ও জাহেলিয়াতের, হক ও বাতিলের এ দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষই দেখতে পাই। ইসলাম-বিরোধী খোদাদ্রোহী শক্তির দ্বারা সত্যের পতাকাবাহীগণ নির্যাতিত-নিষ্পেষিত হলেও অবশেষে বাতিল শক্তিই ধ্বংস হয়েছে।
বিশ্বনবীর আগমন
ইসলাম ও জাহেলিয়াতের দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষের এক পর্যায়ে সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে ইসলামের দাওয়াত নিয়ে মক্কা শহরে আবির্ভূত হলেন বিশ্বনবী মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তখন আরবসহ সারা বিশ্ব ছিল জাহেলিয়াতের ঘন অন্ধকারে নিমজ্জিত।
নবী মুস্তাফাকে (সা) আল্লাহতায়ালা মানবজাতির জন্যে সর্বশেষ নবী হিসেবে প্রেরণ করেন এবং মানবজাতির জন্যে তাঁর সর্বশেষ হেদায়েতনামা তথা পথনির্দেশনা পাঠান। সর্বশেষ নবী এবং সর্বশেষ হেদায়েতনামা এ কথাই প্রমাণ করে যে, মানুষের সার্বিক কল্যাণের জন্য একটি পূর্ণাংগ দ্বীন বা জীবন-বিধানই উপস্থাপিত করা হয়। এ কারণেই দ্বীনের নাম রাখা হয় ‘আল ইসলাম’ যার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তার জন্যে অবতীর্ণ মহাগ্রন্থ আল কুরআনের দাওয়াত উপস্থাপনের সহজ বোধগম্য প্রকাশভঙ্গিমা।
কুরআন তার দাওয়াত উপস্থাপনে আদেশব্যঞ্জক ভাষার পরিবর্তে উপদেশমূলক ভাষা ব্যবহার করলেও তার সাথে বলিষ্ঠ যুক্তি-প্রমাণও পেশ করেছে। কুরআন মানুষের মনে যে বিশ্বাস জন্মাতে চায়- তার সত্যতাকে প্রমাণ করার জন্যে বলিষ্ঠ যুক্তিসহ তা হৃদয়গ্রাহী ভাষায় পেশ করে। সে যুক্তি-প্রমাণ বিভিন্ন ধরনের হয়- বুদ্ধিবৃত্তিক, প্রাকৃতিক, সজ্ঞামূলক এবং ঐতিহাসিক। বলিষ্ঠ যুক্তি-প্রমাণসহ দাওয়াত পেশ করা এ কথারই প্রমাণ যে, কুরআন মানুষের বুদ্ধি-বিবেকের কাছেই তার আবেদন রাখে। যেমন-
“নিশ্চয়ই আসমান ও যমীন সৃষ্টির মধ্যে এবং রাত ও দিনের আবর্তনে অসংখ্য নিদর্শন রয়েছে বুদ্ধিমান লোকদের জন্যে”- (আলে ইমরানঃ ১৯০)।
এ ধরনের আয়াত কুরআন পাকে বহু আছে যার থেকে এ কথা সুস্পষ্ট হয় যে, মানুষ একটি বুদ্ধি-বিবেকসম্পন্ন সত্তা হওয়ার কারণেই তাকে দাওয়াত গ্রহণের যোগ্য গণ্য করা হয়েছে। অর্থাৎ যে কেউ তার জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেককে সঠিকভাবে ব্যবহার করবে, এ দাওয়াতের সত্যতা তার নিকটে সুস্পষ্ট হয়ে যাবে। সত্যানুসন্ধিৎসা এবং নিষ্ঠা সহকারে চিন্তা ভাবনা করলে কেউ এ সত্যের আলোক থেকে বঞ্চিত থাকতে পারে না।
জাহেলিয়াতের আঁধারে আচ্ছন্ন পরিবেশ
যুক্তিপ্রমাণ, ঐতিহাসিক সাক্ষ্য ও বিভিন্ন নিদর্শনাদিসহ হৃদয়গ্রাহী ভাষায় ইসলামী দাওয়াত পেশ করা সত্ত্বেও অতীতের ন্যায় আরবের জাহেলিয়াতও এ দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করে। তার কারণ, সমাজে জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেক ও অন্তর্দৃষ্টির অভাব ছিল। সূর্য উদিত হলে তার আলো চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এ আলোক থেকে তারাই সুযোগ সুবিধা লাভ করতে পারে, যাদের দৃষ্টিশক্তি থাকে। যে অন্ধ অথবা যে দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছে, তার জন্যে সবকিছুই ঘন আঁধারে আচ্ছন্ন মনে হয়। অন্তর্দৃষ্টির বেলায়ও তা-ই হয়ে থাকে। এ অন্তরের চক্ষু যদি দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলে অথবা তার উপর যদি ছানির ন্যায় মোটা পর্দা পড়ে থাকে, তাহলে সে সত্যকে দেখতে পায় না। শেষ নবীর আগমনের সময় সমাজ এ ধরনের অন্ধ ও বধির লোকেই পরিপূর্ণ ছিল। নিম্নের ভাষায় কুরআন সে সময়ের অবস্থা বর্ণনা করেছে-
“তাদের তো মন আছে, কিন্তু তা দিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে না। চোখ আছে বটে কিন্তু তা দিয়ে দেখে না। তাদের কান আছে, তা দিয়ে শুনে না। তারা পশুর ন্যায় বরং তার চেয়েও অধিক পথভ্রষ্ট ও বিভ্রান্ত। তারা চরম গাফলতির মধ্যে ডুবে আছে”- (আ’রাফঃ ১৭১)।
এ কথার অর্থ এই যে, এসব লোক- যাদের সামনে নবী মুহাম্মাদ (সা) ইসলামের দাওয়াত পেশ করলেন, দাওয়াতে হক সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করার যোগ্যতাই হারিয়ে ফেলেছে। সত্যতা ও প্রত্যেক বিষয়ের সঠিক তত্ত্ব লাভের জন্যে আল্লাহতায়ালা যেসব উপায়-উপকরণ তাদেরকে দিয়েছেন, তার মাধ্যমে অন্য সবকিছুই তারা করছে, কিন্তু প্রকৃত কাজটি তারা করছে না যা তাদের করা উচিত ছিল। অর্থাৎ সত্যকে উপলব্ধি করা। তাদেরকে চক্ষু তথা দৃষ্টিশক্তি এ জন্যে দেয়া হয়েছিল যে, তার দ্বারা তারা বিশ্বজগতের প্রকৃত তত্ত্বসমূহ পর্যবেক্ষণ করবে। শ্রবণশক্তি এ জন্যে দেয়া হয়েছিল যে, সত্যের দাওয়াত মনোযোগ দিয়ে শুনবে এবং সে সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করবে। মন বা বোধশক্তি এ জন্যে দেয়া হয়েছিল যে, চোখ দিয়ে যা তারা পর্যবেক্ষণ করলো এবং কান দিয়ে যা শুনলো দায়িত্বানুভূতিসহ তার সঠিক মূল্যায়ন করে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছবে। কিন্তু তারা চতুষ্পদ পশুর ভূমিকাই পালন করলো। পশু তার চক্ষু ও কর্ণের দ্বারা যতোটুকু জ্ঞান লাভ করে, তারাও তা-ই করে। এসব চতুষ্পদ জন্তুর অবস্থা এই যে, রাখাল বা তাদের মালিক তাদেরকে চিৎকার করে কিছু বলে, তারা বুঝতে পারে না আসলে কি বলা হচ্ছে। তবে এতোটুকু অনুভব করতে পারে যে, কেউ আওয়াজ দিচ্ছে। ইসলামের দাওয়াতের ব্যাপারে এই একই অবস্থা আরবের মুশরিক-কাফেরদের। তারা তার সপক্ষে দেখাশুনা ও চিন্তাভাবনা করার শক্তি একেবারে হারিয়ে ফেলেছে। আহবানকারীর কথার অর্থ হাওয়ায় বিলীন হয়ে যায়। কুরআন পাক তাদের মানসিক অবস্থার চিত্র এভাবে এঁকেছে-
“যারা খোদার পথে চলতে অস্বীকার করেছে তাদের অবস্থা এরূপঃ রাখাল জন্তুগুলিকে ডাকে, কিন্তু তারা এ ডাকের আওয়াজ ব্যতীত আর কিছু শুনতে পায় না। তারা বধির, বোবা ও অন্ধ। এ জন্যে কোন কথা বুঝতে পারে না”- (বাকারাহঃ ১৭)।
অন্য এক স্থানে বলা হয়েছে-
“এরা কি কুরআন সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করে না? অথবা এদের মনের (দরজায়) কি তালা লাগিয়ে দেয়া হয়েছে?”- (মুহাম্মাদঃ ২৪)।
উপরোক্ত আয়াতের অর্থ এই যে, তারা কুরআন সম্পর্কে মোটেই চিন্তাভাবনা করে না। আর যদি বা কখনো করেও, তো তার মর্ম ও তাৎপর্য তাদের হৃদয়ের গভীরে প্রবেশ করে না। তার কারণ এই যে, তারা সত্যকে গ্রহণ করতেই চায় না। তাদের হৃদয়ের প্রবেশপথ তালাবদ্ধ থাকে। তারপর তাদের আর ভালোমন্দ বুঝবার কোন শক্তিই থাকে না। আর এটাই হচ্ছে হৃদয়ের অন্ধত্ব।
অন্ধত্বের কারণ
এ অন্ধত্বের প্রথম কারণ হচ্ছে, জাতীয় এবং পারিবারিক গোঁড়ামি। তাদের কথা হলো এই, যে ধর্মীয় বিশ্বাস, রীতিনীতি ও রসম-রেওয়াজ তাদের পূর্বপুরুষ থেকে চলে আসছে তা-ই সঠিক। কারণ তারা ভুল করে থাকবেন এমনটি তো হতে পারে না। অতএব নবী মুহাম্মাদের (সা) নতুন দ্বীনের দাওয়াত যদি আমরা প্রত্যাখ্যান করি তাহলে তাই হবে আমাদের সৌভাগ্যের কারণ এবং পূর্বপুরুষদের ধর্মত্যাগ না করে তাদের অভিশাপ থেকেও আমরা বেঁচে যাব।
“আমরা আমাদের বাপ-দাদাকে একটা রীতিনীতির অনুসারী পেয়েছি। আর আমরা তাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলেছি”- (যুখরুফঃ ২৩)।
তাদের সপক্ষে কোন কিতাবে ইলাহীর কোন সনদ নেই। তাদের সনদ শুধু এই যে, এসব কিছু বাপ-দাদার সময় থেকে চলে আসছে। অতএব তারা যা যা করেছে আমরাও তাই করব। উল্লেখ্য যে, নবীগণের মুকাবিলায় দাঁড়িয়ে বাপ-দাদার অন্ধ অনুকরণের পতাকা বুলন্দকারী প্রত্যেক যুগে সমাজের বিত্তশালী লোকেরাই কেন ছিল? তার একটি কারণ ছিল যে- দুনিয়ায় ভোগ-সম্ভোগে তারা এতোটা মত্ত ছিল যে, হক ও বাতিলের বিতর্কে মাথা ঘামাবার জন্যে তারা মোটেই প্রস্তুত ছিল না- পাছে বিলাসী জীবন যাপনে কোন ছেদ পড়ে। দ্বিতীয় কারণ এই যে, সমাজে প্রচলিত ব্যবস্থার সাথে তাদের স্বার্থ ওতপ্রোত জড়িত ছিল। নবীগণের উপস্থাপিত ব্যবস্থা দেখার পরই তারা বুঝে নিয়েছিল যে, এ ব্যবস্থার অধীনে তাদের নেতৃত্ব ও প্রভাবপ্রতিপত্তি শেষ হয়ে যাবে এবং অন্যায়ভাবে তারা যতো কিছু ভোগ করছে তার সকল পথ রুদ্ধ হয়ে যাবে।
পূর্বপুরুষদের অন্ধ আনুগত্যই শুধু তাদেরকে সত্য গ্রহণ করা থেকে বিরত রাখেনি, বংশীয় গোঁড়ামি এবং বংশীয় স্বার্থও তাদেরকে ইসলামী দাওয়াত গ্রহনে বাধা দিয়েছে। কুরাইশ গোত্রের বনী কুসাই শাখাটির সাথে নবী পরিবার সম্পৃক্ত ছিল। সেজন্যে বনী কুসাই-এর বিরুদ্ধে অন্যদেরকে ক্ষিপ্ত করে দেয়া হয়। অন্যান্যরা এ জন্যে নবী মুহাম্মাদের (সা) নবুওত মেনে নিতে অস্বীকার করে যে, বনী কুসাই-এর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হবে।
বদরের যুদ্ধের সময় আবু জেহেলের জনৈক সাথী আখনাস বিন শুরাইক নির্জনে আবু জেহেলকে জিজ্ঞেস করে, “সত্যি করে বলতো, মুহাম্মাদকে সত্যবাদী মনে কর, না মিথ্যাবাদী?”
জবাবে সে সুস্পষ্ট ভাষায় বলে, “খোদার কসম, মুহাম্মাদ একজন সত্যবাদী লোক, যে জীবনে কখনো মিথ্যা বলে নি। কিন্তু লিওয়া (১) সিকায়েত (২) হেজাবাত (৩) এবং নবুওত সবই যদি বনী কুসাই’-এর অংশে এসে যায়, তাহলে তুমিই বল, অন্যান্য কুরাইশদের জন্যে কী রইলো?”
নবী (সা)-এর চাচা আবু তালিবের মতো লোকও শুধু এ জন্যে ইসলাম গ্রহণ করতে পারেননি যে, বাপ-দাদার ধর্মের প্রতি অন্ধ বিশ্বাস তাকে ইসলাম গ্রহণের অনুমতি দেয়নি। অথচ নবীর প্রতি তার স্নেহ-ভালবাসা ছিল অতুলনীয়। দুশমনদের মুকাবিলায় তিনি ছিলেন ঢালস্বরূপ। কিন্তু নবীপাকের বার বার অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি কালেমা উচ্চারণ করেননি। নবী (সা) তাকে কত ভক্তি ও দরদের সাথে বলেন, “চাচাজান, আপনি একবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে ফেলুন। তাহলে কিয়ামতের দিন আমি সাক্ষ্য দেব এবং আপনার মাগফেরাতের জন্যে আরজ করব।”
আবু জেহেল এবং অন্যান্য মুশরিক নেতারা সেখানে উপস্থিত ছিল। তারা বললো, “আবু তালিব, মৃত্যুর ভয়ে কি তুমি বুযর্গ পিতা আব্দুল মুত্তালিবের দ্বীন পরিত্যাগ করবে?”
তাদের জাহেলিয়াতের তীর তার লক্ষ্যস্থানে পৌঁছে গেল। আবু তালিবের মধ্যে পিতৃপূজার তীব্র অনুভূতি জাগ্রত হলো এবং তিনি বললেন, আমি আব্দুল মুত্তালিবের দ্বীনের উপরেই মৃত্যুবরণ করছি। ইবনে হিশাম তার ইতিহাসে এ ঘটনাটি বিবৃত করেছেন।
উপরোক্ত দু’টি ঘটনা থেকে একথা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, আরব সমাজে জাতীয়, দলীয়, গোত্রীয় ও পারিবারিক গোঁড়ামি ও অন্ধঅনুসৃতি কতো প্রকট ছিল এবং কায়েমী স্বার্থের জন্যে তারা সত্যকে, নবীর দাওয়াতকে, কল্যাণের পথকে কিভাবে নির্দ্বিধায় প্রত্যাখ্যান করেছে।
দ্বিতীয় কারণ হলো বুদ্ধিবৃত্তিক অন্ধত্ব ও প্রবৃত্তিপূজা। প্রবৃত্তিপূজার প্রবণতা তাদের শিরা-উপশিরায় পরিব্যপ্ত ছিল। প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে তারা বিভিন্ন পন্থা পদ্ধতি ও রীতিনীতি আবিষ্কার করতো এবং তার উপরে মনোমুগ্ধকর লেবাস পরিয়ে দিত। তাকে বৈধ করার যুক্তিপ্রমাণ সরবরাহ করা হতো। মদ্যপান, জুয়া, সুদ, নগ্নতা, অশ্লীলতা, নৃত্যগীত, যৌন অরাজকতা, খুনখারাবি, সন্তান হত্যা প্রভৃতির জন্যে কোথাও প্রকৃতিসুলভ দাবি, কোথাও অর্থনৈতিক কল্যাণ, কোথাও চারুশিল্প এবং কোথাও ধর্মীয় পবিত্রতার পোশাক পরিয়ে দেয়া হতো। এভাবে শয়তানী কামনা-বাসনা এবং ঘৃণ্য ক্রিয়া-কর্মের ভারে মানব প্রকৃতি এমনভাবে নিষ্পিষ্ট হয়ে পড়েছিল যে, এসবের বিরুদ্ধে টু শব্দ করতে পারতো না। ইসলাম যেহেতু এসবের লাইসেন্স দিতে পারে না, বরং এসবের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়, সেজন্যে একে তারা তাদের জন্যে বিপদ মনে করে। একে তারা তাদের উপর ভয়ানক জুলুম-অবিচার মনে করে। কারণ তারা প্রকৃতপক্ষে তাদের প্রবৃত্তিকেই খোদা বানিয়ে নিয়েছিল। তাদের এ মানসিকতা ও আচরণে রহমতের নবী যখন হৃদয়ে বেদনাবোধ করতে লাগলেন, তখন আল্লাহতায়ালা বলেন-
“তুমি কখনো সে লোকের অবস্থা চিন্তা করে দেখেছ, যে নিজের প্রবৃত্তিকে তার খোদা বানিয়ে নিয়েছে? এমন লোককে সৎপথে আনার দায়িত্ব তুমি নিতে পার কি?”- (ফুরকানঃ ৪৩)।
প্রবৃত্তিকে খোদা বানিয়ে নেবার অর্থ তার বন্দেগী-দাসত্ব করা এবং বাস্তব অবস্থার দিক দিয়ে এটাও মূর্তিপূজার মতোই শির্ক। হযরত আবু উমামা (রা) বর্ণিত হাদীসে নবী (সা) বলেন, এ আসমানের নিচে আল্লাহ ছাড়া আর যতো মাবুদের পূজা করা হয় তাদের মধ্যে সর্বনিকৃষ্ট মাবুদ হচ্ছে প্রবৃত্তি যার হুকুম মেনে চলা হয়- (তাবারানী)।
যে ব্যক্তি তার প্রবৃত্তিকে বিবেকের অধীন রাখে এবং বিবেকসম্মত ফয়সালা করে, সে যদি কোন প্রকার শির্ক ও কুফরে লিপ্ত হয়, তাহলে তাকে বুঝিয়ে-শুনিয়ে সঠিক পথে আনা যায়। কিন্তু প্রবৃত্তির দাস লাগামহীন উটের মতো এবং তাকে কিছুতেই সংশোধন করা যায় না। প্রবৃত্তি তাকে যেদিকে পরিচালিত করে সেদিকেই চলে।
তৃতীয় হচ্ছে পূর্ব থেকে প্রচলিত রসম-রেওয়াজ। এসবের বিরুদ্ধে কোন কথা শুনতে তারা রাজি নয়, এতোকাল থেকে যে রীতিনীতি চলে আসছে তা পরিহার করার চিন্তাও তারা করতে প্রস্তুত নয়।
উপরোক্ত তিনটি বস্তু দুরারোগ্য ব্যাধির ন্যায় তাদের মন-মস্তিষ্ক আক্রান্ত করে রাখে। সত্যের আহবান তারা শুধু প্রত্যাখ্যানই করে না, বরং সত্যের আওয়াজ তাদের রাগ বর্ধিত করে।
“আমরা তো এ কুরআনের মধ্যে বিভিন্নভাবে দ্বীনের মর্মকথা বর্ণনা করেছি যাতে করে তারা হৃদয়ঙ্গম করে সচেতন হয়, কিন্তু প্রকৃত সত্য থেকে তারা আরও দূরে পালিয়ে যাচ্ছে”- (বনী ইসরাইলঃ ৪১)।
জাহেলিয়াতের মানসপুত্র এ ধরনের লোক সকল যুগেই পাওয়া যাবে।
জাহেলিয়াতপন্থীদের প্রতিক্রিয়া
নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওত ঘোষণার সাথে সাথে মক্কার মুশরিক-কাফেরদের প্রতিক্রিয়া পর্যায়ক্রমে তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে। প্রথমে এ ঘোষণা তাদের কাছে এক চরম বিস্ময় বলে মনে হয়। তাদের দৃষ্টিতে যে মানুষটি ছিলেন সমাজে সবচেয়ে ভালো মানুষ, সত্যবাদী, পরম বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য এবং অতুলনীয় চরিত্রের অধিকারী, তার মুখে এমন অবাস্তব ও অবান্তর কথা কেন?
“আল্লাহ কি একজন মানুষকে তাঁর রসূল করে পাঠালেন?”- (বনী ইসরাইলঃ ১৪)।
“তাদের কাছে এটা এক বিস্ময়ের ব্যাপার ছিল যে, একজন সাবধানকারী স্বয়ং তাদের মধ্য থেকে (মানুষের মধ্য থেকে) এসেছে। ফলে কাফেররা বলতে লাগলো- এ তো বড়ই আজব কথা”- (কাফঃ ২)।
জ্ঞান বিবেক বর্জিত লোকের মতো তারা সর্বত্র এ চাঞ্চল্যকর চর্চা শুরু করলো যে, খোদা নাকি কখনো মানুষকে তাঁর রসূল করে পাঠান। তাদের কথা- আমাদের সর্বজনপ্রিয় সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত লোকটির মুখে যখন এ ধরনের অবান্তর কথা শোনা যাচ্ছে, তখন নিশ্চয় তার মস্তিষ্ক বিকৃত হয়েছে। অথবা জ্বিনে ধরেছে। এভাবে নবী মুহাম্মাদের (সা) বিরুদ্ধে মানুষের মনকে বীতশ্রদ্ধ করে তোলার এক অভিযান শুরু হলো।
তারপর মৃত্যুর পর-জীবনের কথা, আখিরাতের কথা। এ তো তাদের কাছে আরও হাস্যকর-অবিশ্বাস্য।
তাদের ভাষ্য ছিল এরকমঃ “আমরা কি তোমাদেরকে এমন একজন লোকের কথা বলব, (যে তোমাদেরকে এ আজগুবী) খবর দেয় যে, তোমরা যখন (মৃত্যুর পর পচে গলে) ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে, তখন নাকি তোমাদেরকে নতুন করে পয়দা করা হবে?”- (সাবাঃ ৭)।
এভাবে জাহেলিয়াতের পতাকাবাহীরা ঠাট্টা-বিদ্রুপ-উপহাস সহকারে প্রথমে ইসলামের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করে। পরে তাওহীদ ও আখিরাতকেও তারা অবান্তর বলে প্রত্যাখ্যান করে এ কারণে যে, এ ধরনের অবাস্তব কথা তারা তাদের পূর্বপুরুষদের কাছে কখনো শুনেনি। তারপর নবীর (সা) বিরোধিতা শুরু হয় এবং তা ক্রমশঃ নির্যাতন, নিষ্পেষণের রুপ ধারণ করে। কেউ ইসলাম গ্রহণ করা মাত্র তার উপর মুসিবতের পাহাড় ভেঙ্গে পড়তো। এভাবে মক্কায় অবস্থানকালে মুসলমানদের জীবন যখন দুর্বিষহ হয়ে পড়ে তখন নবী ও ইসলাম দুশমনদেরকে শাসিয়ে দিয়ে আল্লাহ বলেন, যেসব লোক দুষ্কৃতি করছে তারা কি একথা মনে করে নিয়েছে যে, তারা আমাকে ডিঙ্গিয়ে যাবে? বড়ো ভুল সিদ্ধান্তই করেছে- (আনকাবুতঃ ৪)।
এর দু’প্রকার অর্থ হতে পারে। এক- তারা মনে করে নিয়েছে যে, আল্লাহ যে ইসলামী আন্দোলনকে সাফল্যমণ্ডিত করতে চান তা হবে না। বরঞ্চ তারা যে একে মিটিয়ে দিতে চায় তা-ই হবে। দুই- তাদের বাড়াবাড়ির জন্যে আল্লাহ যে তাদের পাকড়াও করতে চান, সেই পাকড়াও থেকে তারা বেঁচে যাবে।
ইসলামের দুশমনরা হরহামেশা এ ধারণাই পোষণ করে যে, ইসলামী আন্দোলন ও আন্দোলনকারীদেরকে তারা দুনিয়ার বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেবে। তাদের এ ইসলাম-বিরোধিতার জন্যে এবং ইসলামপন্থীদের উপর যুলুম নির্যাতনের জন্যে সর্বশক্তিমান আল্লাহ যে তাদেরকে সমুচিত শাস্তি দিতে পারেন একথা তারা মোটেই বিশ্বাস করে না।
কিন্তু তাদের শত বিরোধিতা ও অত্যাচার-নির্যাতন সত্ত্বেও মুসলমানের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধিই পাচ্ছিল। তার প্রধান কারণ আরবি ভাষায় অবতীর্ণ আল্লাহর বাণী আল কুরআন। কুরআনের কতকগুলো সাধারণ গুণ আছে। প্রথমতঃ তা এক অতি উচ্চমানের সাহিত্য, যার সমতুল্য দু’ একটি ছত্র রচনা করাও মানুষের সাধ্যের অতীত। দ্বিতীয়তঃ তার ভাষা প্রাঞ্জল, বোধগম্য, অতি আকর্ষণীয় ও হৃদয়গ্রাহী। শ্রোতার মনে তা বিরাট প্রভাব বিস্তার করে। তার অর্থ ও অন্তর্নিহিত মর্ম শ্রোতার হৃদয়ের গভীরে প্রবেশ করে চিন্তার বিপ্লব সৃষ্টি করে। কুরআনের প্রতিটি কথা যেমন অতীব সত্য তেমনি অকাট্য যুক্তিপূর্ণ। সত্যের একটা আলাদা আস্বাদ থাকে যা সত্যানুসন্ধানীদেরকে সহজেই আকৃষ্ট ও বিমোহিত করে। মানুষের স্বভাব-প্রকৃতি বুদ্ধিমত্তা এবং প্রকৃতিরাজ্য ও তার ব্যবস্থাপনার সাথে, কুরআনের কথাগুলো সামঞ্জস্যশীল ও সংগতিপূর্ণ। তাই যারা মনোযোগ সহকারে কুরআন শ্রবণ করে ও চিন্তা-ভাবনা করে তাদের মনের দুনিয়ায় এক বিপ্লব ঘটে যায় এবং কুরআনের আহ্বানে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাড়া দেয়।
কুরআন শ্রবণে বাধাদান
জাহেলিয়াতের ধারক-বাহক তথা ইসলামের দুশমনরা যখন উপলব্ধি করলো যে, সমাজের সর্বোত্তম ও সকলের শ্রদ্ধাভাজন এক ব্যক্তির মুখে মানুষ এমন সব কথা শুনছে যার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তারা পূর্বপুরুষদের ধর্ম ত্যাগ করছে এবং বর্তমান সমাজ ও তার নেতৃত্বের প্রতি তারা বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ছে, তখন তারা দিশেহারা হয়ে পড়ে এবং আল্লাহর কালাম কুরআনের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়। তারপর তারা কুরআন শ্রবণের বিরুদ্ধে এক নিষেধাজ্ঞা জারি করে। তাদের সম্পর্কে কুরআন বলে,
“সত্যের অমান্যকারীরা বলে, কুরআন কখনো শুনবে না। (আর যখন শুনানো হয়) তখন তোমরা হৈ-হল্লা করে (প্রতিরোধ সৃষ্টি করবে)। তাহলে তোমরা এ কাজে জয়ী হবে।”
আল্লাহ বলেনঃ
“এ সত্য অস্বীকারকারীদেরকে আমরা কঠোর আযাবের স্বাদ গ্রহণ করাবো। আর যে নিকৃষ্টতম কাজ করছে তার পুরোপুরি প্রতিফল তাদেরকে দেব। আল্লাহর দুশমনদের প্রতিফল হলো জাহান্নাম। এর মধ্যেই তারা চিরকাল বাস করবে। এ শাস্তি এ জন্যে যে, তারা আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করেছিল।
সত্য অস্বীকারকারী এসব কাফের জাহান্নামে গিয়ে বলবে, হে আমাদের রব, সেই জ্বিন ও মানুষগুলোকে আমাদের একটু দেখিয়ে দাও যারা আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল। আমরা তাদেরকে পায়ের তলায় নিষ্পেষিত করব যেন তারা ভালোমত লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়”- (সূরা হা-মীম আসসাজদাহঃ ২৭-২৯)।
প্রাচীন জাহেলিয়াতের ধারক-বাহকরা যেমন কুরআন প্রচার ও প্রসারকে বরদাস্ত করতে পারেনি এবং তা বন্ধ করার কোন চেষ্টা ও কূট-কৌশলই বাকী রাখেনি, তেমনি আধুনিক জাহেলিয়াতের ধারক-বাহক তথা ইসলামের দুশমনরাও কুরআনকে মোটেই ভালো চোখে দেখতে পারেনি। কিন্তু কুরআন প্রচার বন্ধ করার চেষ্টা কোনদিনই সফল হয়নি, বরঞ্চ উল্টো ফলই হয়েছে। এককালীন ইসলামের ঘোরতর দুশমন হযরত ওমর (রা) নবী মুহাম্মাদকে (সা) হত্যার উদ্দেশ্যে মুক্ত তরবারি হাতে অগ্রসর হয়ে ঘটনাক্রমে পথিমধ্যে কুরআনের কয়েকটি ছত্র পাঠ করে তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন, তাঁর মনের মধ্যে সত্য উদঘাটিত হয়। ফলে নবীর দুশমন নবীপ্রেমে পাগল হয়ে পড়েন। আবিসিনিয়ার খৃস্টান সম্রাট কুরআন পাঠ শুনে আনন্দে অশ্রু সংবরণ করতে পারেননি। নাজরানের খৃস্টান প্রতিনিধিগণ নবী মুহাম্মাদের (সা) পবিত্র মুখ থেকে কুরআন পাঠ শুনে মুগ্ধ হয়ে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে কুরআনের প্রচার ও প্রসার বন্ধের হুমকি দেয়া হয়। কিন্তু ফল উল্টোই হয়েছে। কুরআন পাকের ইংরেজি তর্জমা অসংখ্য অগণিত সংখ্যায় বিশ্বের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে এবং স্বয়ং ইংল্যান্ডের বহু খ্যাতনামা ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং এখনও করছেন। পৃথিবীর সর্বত্র এই একই অবস্থা দেখা যাচ্ছে। ভারত থেকেও চেষ্টা করা হয়েছিল কুরআনকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করার। কিন্তু সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। ভারতের কয়েকটি ভাষায় কুরআনের অনুবাদ হয়েছে। অমুসলিমদের মধ্যেও কুরআন পাঠের আগ্রহ বেড়ে চলেছে। ভারতের বহু উচ্চশিক্ষিত ও পণ্ডিত ব্যক্তি হিন্দুধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করছেন। মুসলিম নামধারী মেকি মুসলমানরাও কিন্তু কাফেরদের অনুসরণে কুরআনের প্রচার-প্রসার বন্ধ করার চেষ্টা করে আসছে। সর্বপ্রথম এ কাজ শুরু হয় তুরস্কে কামাল পাশার শাসনামলে। আরবী বর্ণমালা তুরস্কে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। আরবী ভাষায় অবতীর্ণ কুরআন প্রচার বন্ধ করাই ছিল এর উদ্দেশ্য। কিন্তু সে উদ্দেশ্য সফল হয়নি।
মুসলিম নাম ধারণ করার পর কেউ মেকি মুসলমান হলে অমুসলিম কাফের অপেক্ষা ইসলামের বিরুদ্ধে বেশি সোচ্চার হয়। তাই ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায়, অমুসলিম কাফেরদের দ্বারা ইসলামের যত ক্ষতি হয়েছে মেকি মুসলমান ও মেকি আলেমদের দ্বারা তার চেয়ে অনেক বেশি ক্ষতি হয়েছে।
তবে ইসলামে অবিশ্বাসী কাফের হোক অথবা কাফেরদের মানসিক দাস মেকি মুসলমান হোক তাদের জেনে রাখা দরকার যে, কুরআন আল্লাহতায়ালার শাশ্বত বাণী এবং চিরকাল তাকে আসলরূপে সংরক্ষিত রাখার দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ গ্রহণ করেছেন। তার প্রচার ও প্রসার বন্ধ করা অথবা তাকে সামান্যতম বিকৃত করা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। যারা কুরআন প্রচার বন্ধের নির্দেশ দিচ্ছে এবং এ নির্দেশ অন্ধভাবে পালন করতে গিয়ে যারা মাঠে-ময়দানে নর্তন-কুর্দন করছে, ফ্যাসিবাদী কায়দায় কথা বলছে ও প্রতিরোধ সৃষ্টি করছে, তাদের উপরে বর্ণিত কুরআনের আয়াতের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। আখিরাতে এসব ফ্যাসিবাদী মেকি মুসলিম নেতা ও তাদের অন্ধ অনুসারীদের পরিণাম থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে কুরআনের দিকে আন্তরিকভাবে ফিরে আসাটাই তাদের জন্য মঙ্গলজনক।
জাহেলিয়াতের মুকাবিলায় অবিচল থাকার উপায়
বিশ্বনবী মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাহেলিয়াতের মুকাবিলায় ইসলামের পথে অবিচল থাকার যেসব উপায় পদ্ধতি বলে দিয়েছেন, তার অতি গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটির উল্লেখ নিম্নে করা হলো।
একঃ প্রকৃত বুদ্ধিমত্তা
মানব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামের দৃষ্টিতে সঠিক ভূমিকা পালনের ও জীবনে সাফল্য অর্জনের জন্যে বুদ্ধিমত্তার অনিবার্য প্রয়োজন। আর এ বুদ্ধিমত্তা হতে হবে সুষ্ঠু ও সঠিক চিন্তাপ্রসূত। ইসলামে প্রকৃত বুদ্ধিমত্তা বলতে যা বুঝায় তা হচ্ছে এই যে, মানুষের দৃষ্টি প্রতি মুহূর্তে নিবদ্ধ হয়ে থাকবে খোদার সন্তুষ্টি লাভের উপর। মানুষ যেন এমন কোন আচরণ না করে যা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের চিন্তা থেকে গাফেল ও বিমুখ করে রাখে এবং যা তাঁর অসন্তুষ্টির কারণ হয়। এ কারণেই আল্লাহতায়ালা বার বার মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেন-
“হে বুদ্ধিবিবেকবান লোকেরা! আমাকে ভয় করে চল”- (বাকারাহঃ ১৯৭)।
ভয় তাঁকে এজন্যে করা যাতে তিনি অসন্তুষ্ট না হন। তিনি যেন কখনও অসন্তুষ্ট না হন- একথাটি হরহামেশা মনে রাখা এবং আপন আচরণ দ্বারা তাঁকে সন্তুষ্ট রাখাই প্রকৃত বুদ্ধিমত্তা।
“আসমান ও যমীনের সৃষ্টিতে এবং রাত দিনের আবর্তনে অসংখ্য নিদর্শন রয়েছে সেসব বুদ্ধিমান লোকদের জন্যে যারা চলতে-ফিরতে, ওঠা-বসায় এবং শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে”- (আল ইমরানঃ ১৯০)।
বুদ্ধিবিবেকসহ আসমান ও যমীনের সৃষ্টিরহস্য সম্পর্কে যখন কেউ সঠিক চিন্তাভাবনা করে এবং সেই সাথে যার মনে খোদার ইয়াদ জাগ্রত থাকে, সৃষ্টিজগতের নিদর্শনাবলী জন্তু-জানোয়ারের মতো দেখে না বরঞ্চ চিন্তা-গবেষণা ও পর্যবেক্ষণ করে, সে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঘোষণা করে যে, এ গোটা সৃষ্টিরাজ্য একটা বিজ্ঞতাপূর্ণ ব্যবস্থাপনার অধীন।
চিন্তা ও কাজের এ ধরনকে নবী পাক (সা) তার নিজের কথায় এভাবে বর্ণনা করেনঃ “বুদ্ধিমান তো সে ব্যক্তি যে তার প্রবৃত্তিকে বশীভূত করে রাখে এবং মৃত্যুর পরের জীবনের জন্যে কাজ করে”- (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)।
প্রতিটি কাজের জন্যে আখিরাতে আল্লাহতায়ালার নিকটে জবাবদিহি করতে হবে- এ তীব্র অনুভূতি মনে সদা জাগ্রত থাকলে আল্লাহর অসন্তুষ্টিভাজন কাজ ও আচরণ থেকে বাঁচা যায়। এটাকেই বুদ্ধিমত্তা বলা হয়েছে। নবী মুস্তাফা (সা) বুদ্ধিমত্তার পরিপূর্ণ ধারণাই সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন। মৃত্যুর পরের জীবনের জন্যে কাজ করার অর্থ হলো, দ্বীন ও ঈমানের দাবি যদি এই হয় যে, দুনিয়ার নগদ প্রাপ্য-স্বার্থ ও সুযোগ-সুবিধা প্রত্যাখ্যান করতে হবে তাহলে এ দাবি অবশ্যই পূরণ করতে হবে এবং খোদার সন্তুষ্টি জান-মাল ও আরাম আয়েশ কুরবানী করার দাবি করলে তা দ্বিধাহীন চিত্তেই করতে হবে।
দুইঃ ধন-দৌলত ও মর্যাদা সম্পর্কে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি
ইসলাম এ কথা বলে যে, ধন-সম্পদের মালিক হওয়া ও পদমর্যাদা লাভ করা এবং খোদার প্রিয়পাত্র হওয়া এক জিনিস নয়। একথা ঠিক নয় যে, আল্লাহতায়ালা তাদের উপর সন্তুষ্ট যাদের মধ্যে এ দু’টি পাওয়া যায়। আল্লাহর সন্তুষ্টি সবর্তোভাবে নির্ভরশীল ঈমান ও আমলের উপরে। একজন ধসম্পদ ও পদমর্যাদা থেকে বঞ্চিত থাকা সত্ত্বেও ঈমান ও আমলের বদৌলতে খোদার দৃষ্টিতে সম্মানিত বলে গণ্য এবং তাঁর প্রিয় হতে পারে। অপরদিকে একজন অঢেল ধন-দৌলত ও উচ্চমর্যাদা লাভ করার পরেও তাঁর অভিশপ্ত হতে পারে। কারণ দুনিয়াটা মানবের জন্যে কর্মক্ষেত্র, প্রতিদান ক্ষেত্র নয়। এখানে তাকে কাজ করে যেতে হবে। যার পূর্ণ প্রতিদান সে লাভ করবে আখিরাতে। এখানে কারো সচ্ছল হওয়া একথা প্রমাণ করে না যে, আল্লাহ তার কাজকর্মে খুশি এবং এ কারণে সে তাঁর প্রিয়পাত্র। কারো দুঃখ-দারিদ্র্য একথা প্রমাণ করে না যে, খোদা তার প্রতি অসন্তুষ্ট। অর্থের প্রাচুর্য হোক অথবা দারিদ্র্য, রাজনৈতিক এবং সামাজিক উচ্চমর্যাদা হোক অথবা অপমান ও লাঞ্ছনা হোক এ দু’টি বিষয় বিশেষ উদ্দেশ্যে মানুষকে পরীক্ষা করার খোদায়ী আইনের সাথে সম্পৃক্ত। দুনিয়ার জীবনে মানুষকে বিভিন্নভাবে পরীক্ষা করাই তার সৃষ্টির মুখ্য উদ্দেশ্য। সৃষ্টজগতের সমস্ত ব্যবস্থাপনা এ সত্যের সাক্ষ্যদান করে। যেহেতু এটি ছিল মানবজীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক বিষয়, সেজন্যে কুরআনে হাকীম বার বার একথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য এবং তাকে পরীক্ষা করার খোদায়ী আইনের উপর বিস্তারিতভাবে ও বিভিন্নরূপে আলোকপাত করা হয়েছে। কিন্তু জাহেলিয়াতের সৃষ্ট মানসিকতা তা মেনে নিতে পারেনি। জাহেলিয়াতের এ দৃষ্টিভংগির মধ্যে সেই মানসিকতা অবিচল থাকে যে, ধনসম্পদ ও পদমর্যাদা এবং খোদার সন্তোষ ও ভালবাসা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যে যত বড়ো ধনসম্পদ ও পদমর্যাদার মালিক হবে, সে ততটা খোদার প্রিয় ব্যক্তি হবে। দারিদ্র্য ও পদমর্যাদাহীনতা খোদার অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হওয়ারই নিদর্শন। এ দৃষ্টিভংগির ভিত্তিতে সে সত্যকে সত্যের মাপকাঠিতে বিচার করার পরিবর্তে ধনসম্পদ ও পদমর্যাদার মাপকাঠিতে বিচার করবে। নবী মুহাম্মাদ (সা) যখন তাঁর নবুওতের ঘোষণা করেন, তখন জাহেলিয়াতের মানস সন্তানেরা বিস্ময় প্রকাশ করে বলে যে, তাঁর মর্যাদা তাদের স্বরচিত মাপকাঠি অনুযায়ী ছিল না। তারা বার বার এ কথা বলতে থাকে, প্রথম কথা এই যে, খোদার রসূলের অবশ্যই কোন ফেরেশতা হওয়া দরকার। আর যদি মানুষকেই রসূল হতে হয়, তাহলে তাকে সাধারণ স্তরের মানুষ কিছুতেই হওয়া চলবে না। বরঞ্চ এমন অসাধারণ মর্যাদার হতে হবে যেন আল্লাহতায়ালার মহান সম্পর্কের সাথে তা সংগতিশীল হয়। যেমন, মানুষ রসূল হলে প্রকাশ্যে তার উপর ফেরেশতা নাযিল হতো (সূরা আনআমঃ ৮), নিদেনপক্ষে তার জন্যে (আসমান থেকে) কোন ধনভাণ্ডার নামিয়ে দেয়া হতো, অথবা তার কোন (ফলবান বৃক্ষাদির) বাগান হতো যার থেকে সে প্রচুর জীবিকা অর্জন করতো (ফুরকানঃ ৮)। আর এমন অসাধারণ মানুষও যদি না হোত তবে অন্ততপক্ষে কোন ধনাঢ্য ব্যক্তি হতো, কোন কওমের প্রধান হতো, কোন প্রসিদ্ধ গোত্রের সর্দার হতো এবং দৌলত ও পদমর্যাদার মালিক হতো, কিন্তু এখানে ব্যাপারখানা অন্যরকম। একজন অতি সাধারণ মানুষ দাবি করে বসলো যে, সে খোদায়ে যুলজালালের প্রেরিত- অথচ এ দাবি করার কোন গুণাবলীই তার মধ্যে নেই। একদিকে সে সমগ্র জাহানের রহমত হওয়ার দাবি করছে, আর অপরদিকে নিজেই বাজার থেকে সওদা খরিদ করে আনছে। তার কোন চাকরবাকরও নেই, যে জন্যে নিজেকেই সব কাজ করতে হয়।
তারা আরও বলে, এ কুরআন দু’টি প্রসিদ্ধ জনপদের (মক্কা ও তায়েফ) কোন বিশিষ্ট নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির উপর কেন নাযিল করা হলো না? (যুখরুফঃ ৩১)।
এ ধরনের কত অবান্তর কথা তারা নবী মুহাম্মাদ (সা) সম্পর্কে বলতেই থাকে। আল্লাহর প্রিয়পাত্র হতে হলে তাকে অবশ্যই জীবনযাপনের যাবতীয় সামগ্রী, ধনদৌলত ও পদমর্যাদা লাভ অবশ্যই করতে হবে- এ ছিল তাদের বদ্ধমূল ধারণা। অতঃপর মক্কা বিজয়ের সেই শুভদিন যে বিপ্লব সংঘটিত করলো, তার ফলে তাদের চিন্তা ও দৃষ্টিভংগির ভ্রম দূর হয়ে গেল।
তিনঃ গোটা জীবনে ইসলামের অনুসরণ
ইসলাম দুনিয়াকে এ কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে যে, বিশ্বস্রষ্টা মানুষকে বিনা উদ্দেশ্যে পয়দা করেননি। বরঞ্চ তাঁর দাসত্ব আনুগত্যের জন্যেই পয়দা করেছেন, যাকে ইসলামী পরিভাষায় ইবাদাত-বন্দেগী বলে। এ বন্দেগীর অর্থ গোটা জীবনকে আল্লাহতায়ালার হেদায়েত ও মর্জি অনুসারে পরিচালিত করা। এ বন্দেগী শুধু এমন নয় যে, ইবাদাতখানায় আল্লাহর কিছু পূজা-অর্চনা এবং সেইসাথে কিছু ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করা হবে, তারপর সমগ্র জীবন যেমন খুশি তেমনভাবে কাটিয়ে দেয়া হবে। এ আংশিক বন্দেগী আল্লাহতায়ালার সার্বিক ও নিরংকুশ আনুগত্যের অধিকারী হওয়ার মর্মকথার সাথে সংগতিশীল নয়। আর না এটা তাঁর নাযিল করা দ্বীন ও হেদায়েতনামার সাথে সামঞ্জস্যশীল। এ উদ্দেশ্যে ইসলাম যখন জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে খোদাপরস্তির বাস্তব প্রতিফলন দাবি করলো এবং মানুষের সকল চিন্তা-চেতনা ও কর্মের উপর সত্য ও সততার বন্ধন আরোপ করতে লাগলো তখন জাহেলিয়াতের ধারক-বাহকগণ বিস্ময় প্রকাশ করে বিদ্রুপবাণ ছুড়তে লাগলো। ধর্মের যে জাহেলী ধারণা তাদের মনমস্তিষ্ক আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, এবং যেভাবে তারা ধর্মকে জীবনের এক অতিরিক্ত অংশ মনে করেছিল, তার মুকাবিলায় যখন তারা দেখলো যে, এ নতুন দ্বীন মনের স্বাধীনতার মোড়ে প্রহরী নিয়োগ করছে, পদে পদে পুরস্কার ও শান্তির সাহস শুনিয়ে দিচ্ছে, জীবনের বিভিন্ন সমস্যাগুলোকে একটা সুশৃংখল ও সুদৃঢ় ব্যবস্থাপনার বন্ধনে বেঁধে দিচ্ছে এবং জীবনের এমন কোন ক্ষেত্র নেই যা সে নিয়ন্ত্রণ করতে চায় না, তখন এসব তাদের কাছে বর্বরতাই মনে হলো। যুগ যুগ ধরে তাদের ধর্ম-কর্ম এই ছিল যে, স্বহস্তে নির্মিত প্রতিমাগুলোকে কখনো কখনো সিজদা করতো, তাদের জন্যে উট ও ভেড়াছাগল উৎসর্গ করতো, উৎসর্গিত পশুর রক্ত পূজামন্দিরের দেওয়ালে লেপন করতো, কাবা ঘরের পাশে গিয়ে শিস ও হাততালি দিত, ধর্মীয় মেলা-পার্বণ ও রং তামাশা করতো। এ সবই ছিল তাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান। তারপর জীবনের অবশিষ্ট সময়ে লুটতরাজ, হত্যা, ব্যভিচার, মদ্যপান, সুদী কারবার প্রভৃতি গর্হিত কাজে লিপ্ত থাকতো।
এ ছিল জাহেলিয়াতের ধর্ম সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা। জীবনের অতি সংকীর্ণ পরিসরে কিছু ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান (যদিও তা সুষ্ঠু ও মার্জিত চিন্তা ও যুক্তিভিত্তিক ছিল না) আর জীবনের বৃহত্তর পরিসরে ধর্মহীনতা এবং অনাচার-পাপাচারের অবাধ স্বাধীনতা। এটাকেই আধুনিক পরিভাষায় সেকিউলারিজম তথা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ বলা হয়, এ চিন্তাধারা ও দর্শন জাহেলিয়াতের, ইসলামের নয়। নবী পরম্পরার সর্বশেষ নবী ও বিশ্বনবী মুহাম্মাদ মুস্তাফার (সা) বিপ্লবী ঘোষণা এই ছিল যে, ইসলাম মানব জাতির জন্যে এক পূর্ণাংগ জীবনব্যবস্থা। অর্থাৎ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ও মুহূর্তে নিজেদেরকে আল্লাহর আনুগত্যের অধীন করে দিতে হবে। সমাজ, রাষ্ট্র, শিক্ষা-দীক্ষা, সভ্যতা-সংস্কৃতি, শিল্পকলা প্রভৃতি গড়ে উঠবে মানুষের স্রষ্টা ও প্রভু আল্লাহতায়ালার নিরংকুশ আনুগত্যের অধীনে। জাহেলিয়াতের অন্ধ পূজারীগণ এ কথা মেনে নিতে পারেনি। ইবলিস শয়তানেরও এটা মনঃপূত হতে পারে না। কারণ জীবনের সর্বক্ষেত্রে না হলেও কোন কোন ক্ষেত্রে সে মানুষের আনুগত্য লাভের প্রত্যাশী। যে সব ক্ষেত্রে আল্লাহর আনুগত্য অস্বীকার করা হবে, সেসব ক্ষেত্রে শয়তানের আনুগত্য ব্যতীত উপায় থাকবে না অথবা আল্লাহর স্থলে অন্য কারো আনুগত্য করতে হবে। আর গায়রুল্লাহর আনুগত্যকে সবচেয়ে বড় পাপ (শির্ক) বলা হয়েছে। জাহেলিয়াত মানুষকে শির্ক থেকে বেঁচে থাকতে দেয় না।
চারঃ মানব জাতির ঐক্য
ইসলাম বলে সকল মানুষ একই মা-বাপের সন্তান। আল্লাহ বলেন, “হে মানব জাতি! তোমাদের সেই প্রভুকে ভয় কর যিনি তোমাদেরকে একটি ‘প্রাণ’ থেকে পয়দা করেছেন। তার থেকেই তার জুড়ি তৈরি করেছেন এবং উভয় থেকে দুনিয়ায় বহুসংখ্যক পুরুষ ও নারীও ছড়িয়ে দিয়েছেন”- (সূরা নিসাঃ ৩)।
যেহেতু সকল মানুষের মূল এক এবং সকলে পরস্পরে একই পরিবারের সদস্যের ন্যায় সে জন্যে বংশ, গোত্র, বর্ণ ও ভাষার ভিত্তিতে তাদের মধ্যে কেউ উচ্চ ও নীচ অথবা কুলীন ও অকুলীন হতে পারে না। প্রকৃত ব্যাপার যখন এই তখন বর্ণ, বংশ, দেশ ও জাতীয়তার ভিত্তিতে কারো উপরে কারো শ্রেষ্ঠত্ব হতে পারে না। এর কোনটিই গর্ব অহংকারের কোন কারণ হতে পারে না। এ ভ্রান্ত ধারণা খণ্ডন করে নবী মুহাম্মাদ (সা) ঘোষণা করেন- সকল মানুষ আদমের সন্তান এবং আদমকে মাটি থেকে পয়দা করা হয়- (তিরমিযী)।
তিনি আরও বলেন, “হে মানবজাতি! তোমাদের সকলের রব মাত্র একজন। একমাত্র খোদাভীরুতা ব্যতীত অন্য কোন কারণে কোন আরববাসীর শ্রেষ্ঠত্ব নেই কোন আজমবাসীর উপর, না কোন আজমবাসীর কোন আরববাসীর উপর। আর না কোন কালো কোন সাদা থেকে শ্রেষ্ঠ এবং না কোন সাদা কোন কালো থেকে শ্রেষ্ঠ”- (বায়হাকী)।
নবীর এ বিপ্লবী ঘোষণা কোন খেয়ালী মতবাদ অথবা সুবিধাবাদপ্রসূত ছিল না। বরঞ্চ দৃপ্তকণ্ঠে একটি ঈমান ও আকীদার ঘোষণা ছিল। এমন সময়ের ঘোষণা যখন আরব অনারব নির্বিশেষে মানুষকে বর্ণ, বংশ ও গোত্রের ভিত্তিতে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করে রাখা হয়েছিল। তাদের মধ্যে অনেকে নিজেদেরকে অপর থেকে অতি উচ্চ ও অভিজাত মনে করতো এবং তাদের কাছে অপরের জান মালের কোনই মূল্য ছিল না। বংশীয় আভিজাত্যের গর্বে যারা গর্বিত ছিল, যারা অপরকে দাসানুদাস বানিয়ে রেখে তাদের রক্ত পানি করা শ্রমের বদৌলতে নিজেদের ভাগ্য গড়েছিল তারা এ বিপ্লবী ঘোষণা মেনে নিতে পারে কি করে? কিন্তু জাহেলিয়াতের অন্ধ আবেগে যারা সদা বিভ্রান্ত ছিল না, যাদের মধ্যে সামান্য বিবেক ও বুদ্ধিমত্তা ছিল, তারা এ বিপ্লবী ঘোষণার মধ্যে উপলব্ধি করলো মানবজাতির ঐক্য এবং মানবতার প্রকৃত মর্যাদা। আর ইসলামই মানবতার এহেন মর্যাদার একমাত্র ধারক ও বাহক।
জনৈক কুরাইশ কাফেরের দাসত্বের শৃংখলে আবদ্ধ ছিলেন আবিসিনিয়ার বিলাল (রা)। তিনি ইসলামের বিপ্লবী কালেমা মনে প্রাণে মেনে নিয়ে মুসলমান হন। প্রভু উমাইয়া তার উপর দিনের পর দিন অমানুষিক ও লোমহর্ষক নির্যাতন চালাতে থাকে। সম্ভ্রান্ত কুরাইশ বংশীয় আবু বকর (রা) অপ্রত্যাশিত অধিক মূল্যে বিলালকে খরিদ করে স্বাধীন করে দেন। একজন অকুলীন, একজন দাস, একজন ম্লেচ্ছ মানবতার মহান মর্যাদা লাভ করেন, বহুদিনের গড়া অসাম্যের প্রাচীর ভেঙ্গে সকলের সাথে সমান মর্যাদার অধিকারী হন। হযরত বিলাল (রা) ইসলামের একটি শক্তি-স্তম্ভই ছিলেন না; বরঞ্চ তিনি মুসলিম মিল্লাতের অতীব স্মরণীয়-বরণীয় হয়ে আছেন এবং থাকবেন চিরকাল। এমনি আরও অনেকে দাসত্বের শৃঙ্খল অতিক্রম করে নবী পাকের (সা) দরবারে অন্যান্যের মতো সমমর্যাদা লাভ করেছিলেন।
পাঁচঃ আইনের চোখে সকলে সমান
মানব জাতির ঐক্য ও সাম্যের স্বাভাবিক দাবি এই যে, আইনগত মর্যাদাও সকল মানুষের সমান। আইনের চোখে কেউ বড়ো, কেউ ছোট নয়। ইসলামের ঘোষণা- সকলের জান-মাল-ইজ্জত ও আব্রু সমান শ্রদ্ধার পাত্র। খোদার আইন সকলের উপর সমভাবে প্রযোজ্য। এ আইন মযলুম মানবতার বহুদিনের আর্তনাদ-হাহাকার দূর করে তাদের মানবিক অধিকার নিশ্চিত করে। কিন্তু জাহেলিয়াতের সন্তানেরা এ বিপ্লবী ব্যবস্থায় দিশেহারা হয়ে পড়ে। কারণ তাদের কায়েমী স্বার্থ বিঘ্নিত হয়, তাদের মিথ্যা আভিজাত্যের গর্ব-অহংকারের প্রাসাদ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়। যে প্রথা বহু শতাব্দী যাবত প্রচলিত ছিল তা এই যে, মানুষের মর্যাদা তার বংশ-গোত্র, ধনদৌলত ও পদমর্যাদার মাপকাঠিতে পরিমাপ করা হবে। কোন সম্ভ্রান্ত গোত্রের কোন ব্যক্তির জীবন কোন নিম্নতর গোত্রের বিশটি জীবনের সমান। কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে হত্যা করা হলে, তার বদলায় হত্যাকারীর সাথে তার গোটা পরিবারকে হত্যা করা হতো। এ অবিচারমূলক ব্যবস্থা শুধু কাফের ও মুশরিক সমাজেই প্রচলিত ছিল না, খোদার শরীয়তের দাবিদার আহলে কিতাবদের মধ্যেও সাধারণভাবে প্রচলিত ছিল। তাদের একটা বিধান এমন ছিল যে, কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি চুরি করলে তাকে ছেড়ে দেয়া হতো। কিন্তু সাধারণ লোক চুরি করলে তার উপর শরীয়তের বিধান জারি করা হতো- (বুখারী, দ্বিতীয় খণ্ড; কিতাবুল হুদুদ)।
এরূপে কোন প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি ব্যভিচার করলে তাকে বেত্রাঘাত করার এবং মুখমণ্ডল কালো করে দেয়ার শাস্তি দেয়া হতো। কিন্তু এই অপরাধ কোন সাধারণ মানুষ করলে তাকে শরীয়তের নির্দেশ অনুযায়ী প্রস্তরাঘাতে নিহত করা হতো। (তাফসীরে কুরতুবী)
ইসলাম যে আইনের শাসন কায়েম করে তার ঊর্ধ্বে কেউ থাকতে পারেনি। কাজী (বিচারক) স্বয়ং খলিফার বিরুদ্ধে রায় দিতেও দ্বিধাবোধ করেননি। আইনের এ সাম্য ও সুবিচার জাহেলিয়াতের অনুসারী কাফের-মুশরিক, আহলে কিতাব এবং অনেক নওমুসলিম যারা জাহেলিয়াতের প্রভাবমুক্ত হতে পারেনি- মেনে নিতে পারেনি। তাদের আভিজাত্যের গর্ব-অহংকার তাদেরকে এ সুবিচারপূর্ণ খোদায়ী আইনের সামনে মাথানত করতে দেয়নি। দ্বিতীয় খলিফার শাসন আমলে জাবালা বিন আয়হাম গাসসানী নামক জনৈক ধনাঢ্য ও প্রভাবশালী নওমুসলিম হজ্বে এসেছিল। তাওয়াফের সময় তার চাদরের উপর তায়েফের এক ব্যক্তির পা পড়ে। সে ক্রোধান্বিত হয়ে তাকে এমন জোরে চপেটাঘাত করে যে, তার নাক কেটে রক্ত বেরোয়। হতভাগ্য তায়েফবাসী খলিফা হযরত ওমর (রা)-এর দরবারে নালিশ করে। খলিফা জাবালাকে সম্বোধন করে বলেন, “তুমি ঐ মযলুম ব্যক্তির কাছে কাকুতি-মিনতি করে ক্ষমা চাও। নতুবা বদলার জন্যে তৈরি হয়ে যাও।” জাবালার বিস্ময়ের সীমা রইলো না। তার আভিজাত্যের অহংকার তাকে ইসলামের সাম্য ও সুবিচার মেনে নিতে দিল না। সে মনে করলো, যে আইনে সম্ভ্রান্ত ও অসম্ভ্রান্তের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয় না, সে আইন বুদ্ধিবিবেক ও মানবতার অপমান করে। তারপর সে ইসলাম ত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে যায়।
ছয়ঃ জিহাদের উদ্দেশ্য আল্লাহর কালেমা বুলন্দ করা
ইসলাম যুদ্ধ-বিগ্রহের যে মহান উদ্দেশ্য বর্ণনা করে তার সাথে দুনিয়া পরিচিত ছিল না। আরব-অনারব সর্বত্রই মানুষ যুদ্ধ সম্পর্কে এ ধারণাই পোষণ করতো যে, রাজ্য প্রতিষ্ঠা, তার সম্প্রসারণ এবং মালে-গণিমত হাসিল করাই ছিল যুদ্ধের উদ্দেশ্য। কিন্তু ইসলাম এসে যুদ্ধের এ উদ্দেশ্য একেবারে বদলে দিল। ব্যক্তিগত ও জাতীয় স্বার্থে যুদ্ধ না হয়ে হতে হবে মানবতার কল্যাণের জন্যে এবং এভাবে যুদ্ধ অন্যায় রক্তপাত করার গর্হিত কাজ থেকে ইবাদাতের মর্যাদা লাভ করবে। ইসলাম ঘোষণা করলো যে, দেশ জয় এবং ধনসম্পদ লাভের জন্যে তরবারির ব্যবহার যুলুম, ফাসাদ এবং বিরাট পাপ। তা চরিত্র ও মানবতার জন্যে হলাহলস্বরূপ। তরবারি এ ধরনের গর্হিত কাজের জন্যে ব্যবহার না করে করতে হবে মানবতার কল্যাণের জন্যে, তার সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের জন্যে। তরবারি ধারণকারীর উদ্দেশ্য হবে খোদার সন্তুষ্টি লাভ করা, যিনি অকল্যাণ-অনাচার পছন্দ করেন না। তিনি চান যে দুনিয়ার বুক থেকে ফেৎনা-ফাসাদ, অনাচার-অশান্তি নির্মূল হয়ে যাক। একমাত্র এ উদ্দেশ্যেই তরবারির ব্যবহার ন্যায়সঙ্গত হবে। কোন পার্থিব স্বার্থে এর ব্যবহার সঙ্গত হবে না। সঠিক ও ন্যায়সঙ্গত হবে যদি তা দুনিয়ার স্বার্থ হাসিলের জন্যে করা না হয়, বরঞ্চ করা হয় আখিরাতের কল্যাণের জন্যে। যুদ্ধে যদিও মূল্যবান জীবন বিনষ্ট হতে দেখা যায়, কিন্তু সত্য প্রতিষ্ঠার জন্যে যে যুদ্ধ, তার দ্বারা মানবতা জীবন লাভ করে। যুদ্ধের এই যে মহান ও কল্যাণকর উদ্দেশ্য ইসলাম বর্ণনা করেছে, এ উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখেই এর নামকরণ করা হয়েছে ‘জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ’।
সাহাবায়ে কেরাম (রা) এমন এক পরিবেশ থেকে ইসলামের আদর্শিক পরিবেশে প্রবেশ করেন যে, যুদ্ধের এ মহান উদ্দেশ্য তারা হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন চিন্তা-চেতনার বৈপ্লবিক পরিবর্তনের মাধ্যমে। একটি দৃষ্টান্ত থেকে তা সহজেই অনুমান করা যায়। একবার হযরত আলী (রা) ইসলামের একজন দুশমনের মুকাবিলা করতে গিয়ে তাকে আছাড় দিয়ে মাটিতে ফেলে দেন এবং বুকের উপর বসে তরবারি চালাতে উদ্যত হন। ঠিক এমন সময় সে ব্যক্তি হযরত আলীর মুখে থুথু নিক্ষেপ করে। হযরত আলী (রা) তখন তাঁর হস্ত সংযত করেন এবং বুকের উপর থেকে নেমে আসেন। লোকটি বিস্মিত হয়ে হযরত আলীর এ আচরণের কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, আমি সত্যের জন্যে তোমাকে হত্যা করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তুমি আমার মুখে থুথু দেয়ার ফলে আমার ব্যক্তিস্বার্থ প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে আমাকে উত্তেজিত করে। এ অবস্থায় তোমাকে হত্যা করলে তা সত্যের জন্যে না হয়ে আমার ব্যক্তিস্বার্থের জন্যেই করা হতো এবং তা আমার জন্যে মন্দ পরিণাম বয়ে আনতো। তাই আমি তোমাকে মুক্ত করে দিলাম। এ একটি ঘটনা থেকে যুদ্ধের ইসলামী ধারণা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে এবং এ মানবীয় মনস্তত্ত্বের দৃষ্টিতে সাধারণ সাহাবায়ে কেরামের মন-মানসিকতাও সহজেই অনুমান করা যায়। সাহাবায়ে কেরামের এ দলটি সর্বোচ্চ মানবীয় গুণাবলীতে ভূষিত ছিলেন এবং তাঁদের প্রত্যেকটি কাজকর্ম ছিল ব্যক্তিস্বার্থের ঊর্ধ্বে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে। নিঃস্বার্থতা এবং লিল্লাহিয়াতের তাঁরা ছিলেন মূর্ত প্রতীক। নবীপাকের সান্নিধ্যে থেকে তাঁর সার্বক্ষণিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমেই তাদের মধ্যে এ গুণাবলী সৃষ্টি হয়েছিল। নবীপাক বার বার তাদেরকে এ কথা বলতেন যে, মালে গণিমত লাভের প্রত্যাশায় কেউ যুদ্ধে যোগদান করলে আল্লাহর পক্ষ থেকে তার জন্য কোন প্রতিদান নেই। সুতরাং ব্যক্তিস্বার্থ বা মালে গণিমতের আশায় এসব খোদাপ্রেমিক কি করে নিজেদেরকে তাঁর সন্তুষ্টি থেকে বঞ্চিত করতে পারেন?
ব্যক্তি, দলীয় ও জাতীয় স্বার্থ ব্যতীত অন্য কোন মহান উদ্দেশ্যে কোন দেশে কোন যুগে অতীতে ও বর্তমানে কোন যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে কি? একমাত্র ইসলামই যুদ্ধের উপরোক্ত মহান উদ্দেশ্য ও ধারণা মানব জাতির সামনে পেশ করেছে।
আল্লাহর পথে জান ও মালের ক্ষতি সত্যিকার লাভ
জাহেলিয়াতের দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাধারণা অনুযায়ী যুদ্ধে জান ও মালের ক্ষয়ক্ষতিকে প্রকৃত অর্থে ক্ষয়-ক্ষতি ও লোকসানই মনে করা হতো। ইসলাম এ সম্পর্কে এক বিপরীত ধারণা পেশ করে, যা জাহেলিয়াতের ধারক বাহকদের বিস্মিত ও স্তম্ভিত করে। আল্লাহর পথে যুদ্ধে বা সংগ্রামে যারা জীবন দেয় তাদের জীবন বিনষ্ট হয় না। বরঞ্চ তাদের আত্মা দেহচ্যুত হওয়ার পর এক নতুন ও চিরন্তন জীবন লাভ করে। যুদ্ধে ধন-সম্পদ যা ব্যয় হয়- তা স্থূল দৃষ্টিতে বিনষ্ট মনে হলেও মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের জন্যে তা সংরক্ষিত থাকে।
বিষয়টি সহজেই বোধগম্য হওয়ার কথা নয় বলে কতিপয় সাহাবীর মনেও বিষয়টি অস্পষ্ট ছিল। ওহুদের যুদ্ধে বহু সাহাবীর শাহাদাতের কারণে মুসলমানদের মধ্যে শোকের মর্সিয়া শুরু হয়। তাঁদের সান্ত্বনা দিয়ে বলা হয়-
“আল্লাহর পথে যারা নিহত হয়েছে তাদেরকে মৃত মনে করো না, বরঞ্চ তারা জীবিত। তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে জীবিকা লাভ করছে”- (আলে ইমরানঃ ১৬৯)।
জীবনের দৈর্ঘ্য – দুনিয়ার কোন ফিতা দিয়ে পরিমাপ করা যায় না। জীবনের কোন শেষবিন্দু নেই। যাকে মৃত্যু বলা হয়ে থাকে, তা প্রকৃতপক্ষে জীবনের সমাপ্তি নয়, বরঞ্চ জীবনের এক স্তর থেকে অন্য স্তরে স্থানান্তরের একটি প্রক্রিয়া। ঈমানদারদের এ কথাই মনে করা উচিত যে, স্থানান্তরের এ প্রক্রিয়া আপন শয্যার পরিবর্তে যদি জিহাদের ময়দানে হয়- তাহলে তা ধ্বংস না হয়ে এক চিরন্তন অনিন্দ্যসুন্দর জীবন দান করে। অতঃপর সে এমন এক মহান ও সুখময় জীবন-জীবিকার অধিকারী হয় যা কল্পনার অতীত।
নবীর একটি হাদীসে বিষয়টি সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। মুসনাদে আহমাদে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। তার সারবস্তু এই যে, যে ব্যক্তি নেক আমলসহ দুনিয়া ত্যাগ করে সে এমন এক আনন্দঘন জীবন উপভোগের সুযোগ লাভ করে যে, পুনরায় দুনিয়ায় ফিরে আসার কোন বাসনাই পোষণ করবে না। কিন্তু শহীদান তার ব্যতিক্রম। তারা এ অভিলাষ পোষণ করে যে, পুনরায় তাদের দুনিয়ায় পাঠানো হোক যাতে খোদার পথে জীবন দেয়ার যে পরম আনন্দ- তা সে ভোগ করতে পারে। এ মহাসত্যটি হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করার পর একজন সত্যিকার মুমিন আল্লাহর পথে জীবন দেয়াকেই চরম ও পরম কাম্য মনে করে। আখিরাতের প্রতি বিশ্বাসী নয়, দুনিয়ায় ভোগ বিলাসই যাদের জীবনের কাম্য, EAT, DRINK AND BE MERRY- এ জীবনদর্শনে যারা বিশ্বাসী তারা মৃত্যুকে সবচেয়ে বেশি ভয় করে। পক্ষান্তরে আল্লাহর জন্যে নিবেদিতপ্রাণ মুমিনগণ আল্লাহর পথে স্বেচ্ছায় ও সন্তুষ্টিতে জীবন দিয়ে শাহাদাতের আবেহায়াত পানের জন্যে সর্বদা ব্যাকুল থাকে। জাহেলিয়াত ও ইসলাম জীবনের এই দুই বিপরীতমুখী ধারণা পেশ করেছে। নবী পাকের (সা) নিজহাতে গড়া সাহাবায়ে কেরাম জীবন মৃত্যুর এ ইসলামী ধারণাই পোষণ করতেন। মুষ্টিমেয় মুনাফিক ব্যতীত সকল সাহাবী শাহাদাতের অমৃত পানের আশায় ব্যাকুল থাকতেন। একটি দৃষ্টান্ত থেকে তাঁদের এ ঐকান্তিক অভিলাষের প্রমাণ পাওয়া যায়।
মক্কা বিজয়ের পর নিভৃত পল্লীর জনৈক অশিক্ষিত বেদুঈন বালক ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে চাচার দেয়া বিরাট সম্পদ পরিত্যাগ করে। অতঃপর মায়ের দেয়া একখানা কম্বল দু’টুকরো করে কোন রকমে সতর ও গা ঢেকে ইসলামের নবীর সাথে মিলিত হওয়ার অভিলাষে মদীনা যাত্রা করে। সারারাত্রি অজানা-অচেনা পথ চলার পর ভোর বেলায় মসজিদে নববীতে পৌঁছে যায়। শ্রান্ত-ক্লান্ত ও সারা দেহ ধুলিমলিন। উদ্ভ্রান্ত পাগলের মত দেখতে। পাগলই বটে। ইসলাম ও ইসলামের নবীর জন্যে পাগল হয়ে দুনিয়াকে জলাঞ্জলী দিয়ে মদীনায় হাজির হয়েছে। পথে প্রান্তরে, গিরি-কান্তারে, আকাশে-বাতাসে ইসলামের মধুর সুরধ্বনি তার কানে মধু বর্ষণ করেছে, নবী মুহাম্মাদের নাম শুনে উতলা হয়েছে। কিন্তু দেখেনি সে কোনদিন তার সে প্রেমাষ্পদকে। সারারাত মরুপথ অতিক্রম করে তাই সে এসেছে তার প্রিয়তমের দর্শনে।
বেলালের উচ্চকণ্ঠ- ‘আসসালাতু খায়রুম মিনান নাওম’ ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হলো মদীনার ঘরদোর-গাছপালা ও পাহাড় পর্বতে। আগন্তুকের হৃদয়ের কুঠুরিতেও তা প্রতিধ্বনিত হলো।
একটু পরে রহমতের নবী বেরিয়ে এসে দেখলেন এক আগন্তুক দাঁড়িয়ে। কি যেন পাওয়ার আশায় আকুল। তার চোখমুখে যেন অফুরন্ত জিজ্ঞাসা, মন সত্যের পিপাসায় কাতর।
নবী (সা) স্নেহ ও দরদমাখা ভাষায় বললেন, ‘তুমি কে, কোথা থেকে এসেছ?’
আগন্তুকঃ আমার নাম আব্দুল ওয্যা। শুনেছি এক নতুন নবীর আবির্ভাব হয়েছে। তাঁর প্রেমে পাগল হয়ে এসেছি এতো দূরে। তারপর সে তার সমুদয় পারিবারিক ও বৈষয়িক অবস্থা বর্ণনা করলো।
নবীপাক বললেন, ‘খুব ভালো কথা, তুমি এখন থেকে আমার খাস মেহমান। তুমি আহলে সুফফার একজন। তবে তোমার নাম আজ থেকে আব্দুল্লাহ।’
নবী (সা) সাহাবায়ে কেরামকে বিশেষ তাকীদ সহকারে বললেন, ‘এর ভরণ-পোষণের দায়িত্ব আমার। তোমরা তাকে কুরআন ও ইসলামের তালীম-তরবিয়াত দাও।’
একবার মসজিদে কিছু লোকের নামাযের সময় আব্দুল্লাহ উচ্চস্বরে কুরআন পড়া শিখছিলেন। হযরত ওমর (রা) তাঁকে কড়া ধমক দিয়ে বললেন, ‘আস্তে পড়, দেখ না নামায হচ্ছে?’
রহমতের নবী (সা) হযরত ওমরের কণ্ঠ শুনে দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বললেন, ‘ওমর! ওকে কিছু বলো না। সে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের জন্যে সবকিছু কুরবানী করে এসেছে।’
তার কিছুকাল পরেই তবুকের অভিযানের প্রস্তুতি চলতে লাগলো। নবীর আহ্বানে আল্লাহর পথে দানের প্রতিযোগিতা শুরু হলো সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে। হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা) তাঁর যাবতীয় সম্পদ নিয়ে হাজির হলেন নবীর দরবারে।
আব্দুল্লাহ এসব দানের প্রতিযোগিতা দেখেন। কিন্তু তাঁর দুঃখ যে এ প্রতিযোগিতায় তিনি অংশগ্রহণ করতে পারছেন না। কারণ তিনি যে নিঃস্ব এবং নবীজীর পোষ্য।
আব্দুল্লাহ নীরব থাকতে পারলেন না। তিনি নবীকে বললেন, “হে আল্লাহর রসূল! আপনি তো জানেন আমার দেবার কিছুই নেই। আছে শুধু এ দেহ ও প্রাণ। আমি তা-ই আল্লাহর জন্যে সোপর্দ করলাম। দোয়া করুন যেন শহীদ হতে পারি।”
নবী মুহাম্মাদ (সা) তিরিশ হাজার মুজাহেদীনের এক বাহিনী নিয়ে তবুকের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে যান। আব্দুল্লাহও সংগে রয়েছেন। কিন্তু তিনি শাহাদাতের প্রেরণায় এতোটা অস্থির ও ব্যাকুল হয়ে পড়েছেন যে, পথে একস্থানে নবীর সামনে হাজির হয়ে বলেন, “ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনি হাত তুলে একটু দোয়া করুন যেন এ যুদ্ধে আমি শহীদ হতে পারি।”
নবী তাঁর আন্তরিক জযবা বুঝতে পেরে বললেন, “দেখতো আশে-পাশের কোথাও থেকে কোন গাছের ছাল আনতে পার নাকি?”
আব্দুল্লাহ গাছের ছাল সংগ্রহ করে দিলেন, নবী (সা) সেটা আব্দুল্লাহর হাতে বেঁধে দিয়ে দোয়া করলেন, “আয় আল্লাহ! আব্দুল্লাহর খুন কাফেরদের জন্যে হারাম করে দাও।”
আব্দুল্লাহ এ দোয়া শুনে ব্যাকুল কণ্ঠে বললেন, “হে আল্লাহর রসূল! আমি তো শহীদ হতে চাই, এ দোয়া করলেন কেন?”
নবী বললেন, “আব্দুল্লাহ! এর পরে তুমি যদি জ্বর হয়েও মর, তুমি হবে সত্যিকার শহীদ।”
মুজাহিদ বাহিনী তবুক নামক স্থানে পৌঁছে শিবির স্থাপন করলেন। হঠাৎ সন্ধ্যার পর খবর রটলো যে, আব্দুল্লাহ জ্বরে আক্রান্ত হয়ে প্রাণত্যাগ করেছেন। খবরটি নবীর কানে পৌঁছামাত্র তিনি দাফনের ব্যবস্থা করতে বললেন।
তবুকের ময়দান। অন্ধকার রাত। হযরত আব্দুল্লাহর জন্যে কবর তৈরি হয়ে আছে। হযরত বেলাল (রা) মশাল হাতে দাঁড়িয়ে কবর ও তার পাশ আলোকিত করে রেখেছেন। একজন কবরে নেমেছেন মাইয়্যেতকে ধরে শুইয়ে দেবার জন্যে। দু’জন মিলে মাইয়্যেতকে কবরে নামিয়ে দিচ্ছেন। কবরের মধ্যে দাঁড়ানো ব্যক্তি ধমকের স্বরে উক্ত দু’জনকে বলছেন, “আদাবান ইলা আখাকুমা- তোমাদের ভাইকে ভক্তি শ্রদ্ধার সাথে কবরে নামিয়ে দাও”।
কবরে মাইয়্যেত নামিয়ে দিচ্ছেন নবীর পর মিল্লাতের শ্রেষ্ঠতম দু’ব্যক্তি হযরত আবু বকর (রা) এবং হযরত ওমর (রা)। কবরের ভেতর দাঁড়িয়ে ধমকের স্বরে বলছেন শহীদ সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহর স্নেহশীল অভিভাবক স্বয়ং রহমতের নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম।
মাইয়্যেতকে যথারীতি শুইয়ে রেখে নবী পাক (সা) উপরে উঠে এসে সকলকে বললেন, তোমরা সব সরে যাও।
সাহাবীগণ ভীত, সন্ত্রস্ত হয়ে চারদিকে সরে দাঁড়ালেন। নবীপাক নিজে তাঁর মুবারক হাত দিয়ে চারদিক থেকে বালি, পাথর ও মাটি দিয়ে কবর ঢেকে দিলেন। তারপর হাত তুলে দোয়া করলেন, “পরওয়ারদেগার! আমি আজ সন্ধ্যা পর্যন্ত আব্দুল্লাহর প্রতি খুশি ছিলাম। তুমিও তার প্রতি খুশি থাক।”
হাদীস বর্ণনাকারী আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা) বলেন, আমার মুখ দিয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এ কথাগুলো বেরিয়ে গেল- ‘এ কবরে আব্দুল্লাহ না হয়ে যদি আমি হতাম’।
শাহাদাতের মর্যাদাকে সাহাবীগণ এভাবেই হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন। এ মর্যাদা কোনদিন ম্লান হয়নি। যুগে যুগে আল্লাহর সৈনিকদেরকে শাহাদাতের এ প্রেরণা অকাতরে আল্লাহর জন্যে জীবন দিতে উদ্বুব্ধ করেছে। ইসলামের ইতিহাসে এর অসংখ্য দৃষ্টান্ত রয়েছে।
আধুনিককালে মুসলমানদের চরম অধঃপতনের যুগেও দ্বীন ইসলামের মুজাহিদগণ আল্লাহর পথে অকাতরে জীবন বিলিয়ে দেয়াকে তাদের চরম ও পরম পাওয়া বলে মনে করেন। বৃহৎ পরাশক্তি রাশিয়ার অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্রের মুখে আফগান মুজাহেদীন শাহাদাতের অমৃত পানের আশায় জীবন দিচ্ছেন স্বেচ্ছায় ও সন্তুষ্ট চিত্তে। তাঁদের এ শাহাদাতের বিনিময় তাঁরা মৃত্যুর পরজীবনেই শুধু লাভ করবেন না, এখানেও তাঁদের বিজয় সম্ভাবনা উজ্জ্বল বলে সকলের ধারণা।
অর্থ ও ধন সম্পদ ব্যয়ের ব্যাপারেও ইসলাম ও জাহেলিয়াতের ধ্যান-ধারণা সম্পূর্ণ ভিন্নতর। জাহেলিয়াতের চিন্তাধারা, দৃষ্টিভঙ্গি, চেষ্টা-চরিত্র, আশা-আকাংখা শুধুমাত্র দুনিয়ার জীবনকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়। দুনিয়ার জীবনের পর আরেকটি জীবন আছে, জাহেলিয়াত এ কথা স্বীকার করে না। তাই দুনিয়ার জীবনকে সুখী ও সুন্দর করার, জীবনকে কানায় কানায় উপভোগ করার, সম্মান, খ্যাতি, ক্ষমতা, পদমর্যাদা, কর্তৃত্ব-প্রভুত্ব লাভ করার জন্যে জাহেলিয়াত মানুষকে সদা কর্মতৎপর রাখে। অবশ্য স্বাভাবিকভাবে এসব যে মানুষের লালসার বস্তু তাতেও কোন সন্দেহ নেই। তবে এসবের চেয়েও মহত্তর বস্তু আছে যা মানুষের কাম্য হওয়া উচিত। যেমন কুরআন বলে-
“মানুষের জন্যে তাদের মনঃপূত জিনিস নারী, সন্তান, সোনাচাঁদির স্তূপ, উৎকৃষ্ট ঘোড়া, গৃহপালিত পশু ও ক্ষেতখামার বড়োই আনন্দদায়ক ও লালসার বস্তু বানিয়ে দেয়া হয়েছে। কিন্তু এ সবকিছু প্রকৃতপক্ষে দুনিয়ার সাময়িক ও ক্ষণস্থায়ী জীবনের সামগ্রী মাত্র”- (আলে ইমরানঃ ১৪)।
দুনিয়ার এসব লালসার বস্তুর অত্যধিক মোহে জাহেলিয়াতের পতাকাবাহী ও তাদের অনুসারীগণ মৃত্যুর পরবর্তী চিরন্তন জীবনকে ভুলে যায়।
আল্লাহ বলেন- “প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর (আখিরাত সম্পর্কে) প্রতিশ্রুতি একেবারে সত্য। অতএব এ দুনিয়ার জীবন যেন তোমাদেরকে প্রতারিত করে না রাখে, আর না প্রতারক (শয়তান) তোমাদেরকে আল্লাহর ব্যাপারে ধোঁকা দিতে পারে”- (লুকমানঃ ৩৩)।
উপরে সূরা আলে ইমরানের ১৪ আয়াতে যেসব লালসার বস্তুর উল্লেখ করা হয়েছে তা সব মানুষের পরীক্ষার জন্যে দেয়া হয়েছে। এ সব প্রতারণার সামগ্রী মাত্র। এসব সামগ্রী স্থূলদৃষ্টিসম্পন্ন লোকদেরকে নানান বিভ্রান্তিতে লিপ্ত করে। এ বিভ্রান্তির ফলে কেউ মনে করে এ দুনিয়ার জীবনের পর আর কোন জীবন নেই। অতএব যতো পার এবং যেভাবে পার দুনিয়াকে উপভোগ কর। তার জন্য কোথাও কারো কাছে কোন জবাবদিহি করতে হবে না। কেউ ক্ষমতা মদমত্ত হয়ে মনে করে তার ক্ষমতা, প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব, বিলাসবহুল জীবন যাপন ও অবাধ আনন্দ-সম্ভোগ কোনদিন শেষ হবার নয়, কেউ নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দিক উপেক্ষা করে শুধুমাত্র বৈষয়িক সুযোগ-সুবিধা ও আনন্দ-উচ্ছল জীবন যাপনকে জীবনের লক্ষ্য বানিয়ে নেয়। জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ব্যতীত জীবনের আর কোন উদ্দেশ্য থাকে না। তার ফলে মনুষ্যত্বের মান যতোই হীন ও ঘৃণ্য হোক না কেন, তার কোন পরোয়াই সে করে না। কেউ মনে করে, জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যই সত্য-মিথ্যা, হক ও বাতিলের প্রকৃত মানদণ্ড। যে নীতি ও পন্থা-পদ্ধতি অনুযায়ী কাজ করলে অভীষ্ট বস্তু লাভ করা যায় তাই সত্য, তার বিপরীত সবই মিথ্যা। কেউ আবার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও সুখী জীবন যাপনকে খোদার প্রিয়পাত্র হওয়ার নিদর্শন মনে করে। তার বিশ্বাস, যার জীবন যতো সুখের তা যে কোন অবৈধ আয়েই হোক না কেন, সে খোদার প্রিয়পাত্র। আর যার দুনিয়ার জীবন বড়ো দুঃখ-কষ্টের- তা ন্যায়নীতি ও সত্যসঠিক পথে থাকার কারণে হলেও- আল্লাহ তার উপর অসন্তুষ্ট এবং তার পরিণামও খারাপ হতে বাধ্য। এ ধরনের যতো ভ্রান্ত ধারণা তা বৈষয়িক জীবনের প্রতারণা বলে আল্লাহ উল্লেখ করেছেন।
উল্লেখ্য যে, সূরা লুকমানের উপরোক্ত আয়াতটিতে মানুষকে যে প্রতারণা থেকে আত্মরক্ষার নির্দেশ দেয়া হয়েছে তা আসে দুনিয়ার চাকচিক্যময় জীবন ও শয়তানের পক্ষ থেকে। দ্বিতীয় স্থানে কুরআনে ‘গারুর’ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। ‘গারুর’ বলতে শুধু ইবলিস শয়তানকেই বুঝানো হয়নি, ইবলিসের অনুসারী জ্বিন এবং মানুষকেও বুঝানো হয়েছে। বুঝানো হয়েছে জাহেলিয়াতের ধারক-বাহক ব্যক্তি, দল-গোষ্ঠী ও গোত্রকে; জাহেলিয়াতের শিক্ষা ব্যবস্থা, সমাজ, শিল্পকলা, সংস্কৃতি ও পরিবেশকে। এ সবকিছুই মানুষকে ইসলাম থেকে জাহেলিয়াতের অন্ধকারে টেনে নিয়ে যায়। মানুষের তৈরি নানান ভ্রান্ত মতবাদ ও দর্শন মানুষকে বিভ্রান্ত করে। তাদের মন থেকে খোদা ও আখিরাতের বিশ্বাস মুছে ফেলে দেয়। সমাজ থেকে ন্যায়, সততা, সত্যবাদিতা, দয়া, স্নেহ, ভালোবাসা, পারস্পরিক সহানুভূতি ও সহমর্মিতা, সুবিচার, জান-মাল-ইজ্জত-আব্রুর প্রতি সম্মান-শ্রদ্ধা বিলুপ্ত হয়ে যায়। তখন মানুষের সমাজ আর মানুষের সমাজ থাকে না; হিংস্র পশুর সমাজে পরিণত হয়।
দুনিয়া ও জীবন সম্পর্কে উপরোক্ত ভ্রান্ত ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গি মানুষকে সম্পদ বৃদ্ধি ও জীবনের মান উন্নয়নের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত রাখে। অর্থ ব্যয় সম্পর্কে তাদের নীতি এই হয় যে, যে কাজে এবং যে পথে অর্থ ব্যয় করলে নগদ মুনাফা লাভ করা যেতে পারে, শুধু সে পথেই তারা অর্থ ব্যয় করবে। আল্লাহর পথে ব্যয় করা দু’টি কারণে সে পছন্দ করে না। প্রথম কারণ এই যে, এ ব্যয় নগদ বা তাৎক্ষণিক কোন মুনাফা লাভের কোন নিশ্চয়তা দেয় না। দ্বিতীয়তঃ আখিরাতকে সে বিশ্বাসই করে না। অতএব সেই অবিশ্বাস্য ও অবাস্তব আখিরাতের জন্য অর্থ ব্যয় করা সে নির্বুদ্ধিতা ও অপচয় মনে করে। এ ধারণা-বিশ্বাস একেবারে জাহেলিয়াতের চিন্তাধারার ফসল। অবশ্যি ইসলামের প্রতি ঈমান আনার পরও যাদের ঈমান ততোটা মজবুত হয়নি অথবা জাহেলিয়াতের চিন্তাধারার প্রভাব পুরোপুরি কেটে উঠতে পারেনি তারাও আল্লাহর পথে ব্যয় করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, “খোদার পথে সম্পদ ব্যয় করতে থাক এবং নিজেদের হাতেই নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করো না”- (বাকারাঃ ১৯৫)।
এ কথার মর্ম এই যে, তোমরা যদি আল্লাহর দ্বীনের বিজয়ের জন্যে সম্পদ ব্যয় না কর এবং তাকে জীবনের প্রিয়তম বস্তু মনে করে সঞ্চিত রাখ, তাহলে তা তোমাদের দুনিয়ার জন্যেও ধ্বংসের কারণ হবে এবং আখিরাতের জন্যেও। দুনিয়ায় তোমরা গোলামির জীবন যাপন করবে এবং আখিরাতে জাহান্নামের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ভোগ করবে।
সাতঃ আল্লাহর পথে ব্যয়
আল্লাহর পথে ব্যয় অর্থাৎ আল্লাহর দ্বীনকে একটি বিজয়ী শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করার জন্যে আল্লাহতায়ালা বার বার মানুষের প্রতি আহবান জানিয়েছেন। শুধু তাই নয়, এ ব্যয় সম্পর্কে এক নতুন ধারণা দেয়া হয়েছে। তা হলো এই যে, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে তাঁর পথে যে অর্থসম্পদ ব্যয় করা হবে তা স্থূলদৃষ্টিতে ব্যয়িত হলেও প্রকৃতপক্ষে তা ব্যয়িত ও ক্ষয়িত হয় না। বরঞ্চ তা ব্যয়কারীর পরবর্তী জীবনের সঞ্চয় খাতে (Saving Account) সঞ্চিত থাকে এবং কয়েকগুণ বর্ধিত আকারে ফেরত দেয়া হবে অর্থাৎ তার বিনিময়ে তত পরিমাণে প্রতিদান দেয়া হবে। এ কথাটিই কুরআন পাকের বহু স্থানে বলা হয়েছে।
“এবং নামায কায়েম কর। যাকাত দাও। আর আল্লাহকে উত্তম ঋণ দিতে থাক। যা কিছু ভালো ও কল্যাণ তোমরা নিজেদের জন্যে অগ্রিম পাঠিয়ে দেবে তা আল্লাহর নিকট সঞ্চিত মওজুদরূপে পাবে। এটাই অতীব উত্তম। আর তার শুভ প্রতিফলও অতি বিরাট”- (মুযযাম্মিলঃ ২০)।
“এবং (হে মুসলমানগণ) খোদার পথে লড়াই কর এবং খুব ভালো করে জেনে রাখ যে, আল্লাহ সবকিছু শুনেন এবং সবকিছু জানেন। তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে আল্লাহকে কর্জে হাসানা (উত্তম ঋণ) দিতে প্রস্তুত। তাহলে আল্লাহ তাকে কয়েকগুণ বেশি ফিরিয়ে দেবেন”- (বাকারাহঃ ২৪৪-২৪৫)।
উপরের আয়াতগুলোতে কর্জে হাসানা বা উত্তম ঋণ দানের মর্ম হচ্ছে, নিছক আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্যে তাঁর পথে অর্থসম্পদ ব্যয় করা। তার আগে খোদার পথে লড়াই-এর কথাও বলা হয়েছে। আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্যে যে লড়াই অপরিহার্য তার জন্যে প্রয়োজনীয় অর্থ অবশ্যই সংগ্রহ করতে হয়। এ উদ্দেশ্যে যারা অর্থসম্পদ ব্যয় করে তাদের এ ব্যয়কে আল্লাহ তাঁর নিজের জন্যে কর্জে হাসানা বলে গ্রহণ করেন এবং তা কয়েকগুণে অধিক ফেরত দেয়ার প্রতিশ্রুতিও দেন। একথা ঠিক যে, আল্লাহতায়ালার অর্থের কোনই প্রয়োজন নেই। তিনি কোন কিছুর জন্যে কারো মুখাপেক্ষী নন। বরঞ্চ প্রতিটি সৃষ্টি প্রতি মুহূর্তে তাঁর করুণার মুখাপেক্ষী। আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য মানুষের কল্যাণ করা। এ মহান উদ্দেশ্যে অর্থসম্পদ ব্যয় করা প্রকৃতপক্ষে মানবকল্যাণের জন্যেই করা হচ্ছে। এ কাজকে সর্বোচ্চ মর্যাদা দেয়ার জন্যেই আল্লাহ একে তাঁর জন্যে কর্জে হাসানা বলে আখ্যায়িত করেছেন।
কুরআন পাকে আরও বলা হয়েছে-
“এমন কে আছে যে আল্লাহকে কর্জ দেবে- কর্জে হাসানা? আল্লাহ তা কয়েকগুণ বৃদ্ধি করে ফেরত দিতে পারেন এবং তার জন্যে (ঋণদাতার জন্যে) অতীব উত্তম প্রতিফল রয়েছে”- (হাদীদঃ ১১)।
এ ঋণদান প্রসংগে আল্লাহতায়ালা দু’টি ওয়াদা করেছেন। একটি এই যে তিনি তা কয়েকগুণ বেশি করে ফেরত দেবেন। আর দ্বিতীয় এই যে, তিনি নিজের পক্ষ থেকে অতিরিক্ত উত্তম প্রতিফলও দান করবেন।
আল্লাহতায়ালার এ ওয়াদা কত হৃদয়গ্রাহী, কত আকর্ষণীয়। আর তিনি যে তাঁর ওয়াদা পুরোপুরি পালন করবেন এ দৃঢ় প্রত্যয় প্রত্যেক মুমিন অবশ্যই পোষণ করে।
এ প্রসঙ্গে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে একটি হাদীস বর্ণিত আছে। উপরোক্ত আয়াত নাযিল হওয়ার পর তা যখন সাহাবীগণ নবীপাকের (সা) যবান মুবারক থেকে শুনতে পেলেন, তখন সাহাবী হযরত আবুদ দাহদাহ আনসারী (রা) আরজ করলেন, হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহ কি আমাদের নিকট থেকে ঋণ চান?
হুযুর (সা) জবাবে বললেন, হে আবুদ দাহদাহ! হাঁ, তিনি ঋণ চান।
আবুদ দাহদাহ বলেন, আপনার হাতখানা আমাকে একটু দেখান তো।
নবী পাক (সা) তাঁর হাতখানা উক্ত সাহাবীর দিকে বাড়িয়ে দিলেন। নবীর মুবারক হাতখানা সাহাবী তাঁর হাতের মধ্যে নিয়ে বললেন- আমি আমার বাগানখানি আমার খোদাকে ঋণ দিলাম। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, সে বাগানে ছয়শত উৎকৃষ্ট খেজুরের গাছ ছিল। সে বাগানের মধ্যেই উক্ত সাহাবীর বাড়ি ছিল যার মধ্যে তিনি তাঁর পরিবারসহ বাস করতেন। নবীর সাথে উপরোক্ত কথা বলার পর হযরত আবুদ দাহদাহ (রা) সোজা আপন ঘরে গিয়ে পৌঁছলেন। স্ত্রীকে ডেকে বললেন, দাহদাহর মা! ঘর থেকে বেরিয়ে এসো। আমি এ বাগান আমার খোদাকে ঋণ দিয়েছি।
তাঁর স্ত্রী বললেন, দাহদাহর পিতা! তুমি এটা করে খুবই মুনাফার কারবার করেছ। তারপর তাঁরা তাঁদের যাবতীয় আসবাবপত্র, লটবহর এবং সন্তান-সন্ততিসহ বাগান থেকে বেরিয়ে যান- (ইবনে আবি হাতেম)।
আল্লাহর পথে এমন সর্বস্ব দানের কোন দৃষ্টান্ত ইসলাম ছাড়া অন্য কোথাও পাওয়া যাবে কি? জাহেলিয়াত তো ঠিক এর বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে। জাহেলিয়াতের প্রধান প্রবক্তা ও সর্বাধিনায়ক ইবলিস শয়তান ও তার অনুচরবৃন্দ এ ধরনের দানকে নির্বুদ্ধিতা ও দারিদ্র্যের কারণ বলে তার থেকে মানুষকে বিরত থাকতে বলে।
আল্লাহতায়ালা যখন মুমিন বান্দাদেরকে এ ধরনের ত্যাগের জন্যে উৎসাহিত করেন, তখন শয়তান ও তার অনুসারীগণ বলে, অবাস্তব ও মিথ্যা আশায় ধন-সম্পদ অপচয় করে দারিদ্র্যের অভিশাপ টেনে এনো না। বরঞ্চ জীবনকে উপভোগ করার জন্যে অর্থসম্পদ ব্যয় কর। কারণ মৃত্যুর পরে আর উপভোগ করার কোন সুযোগ হবে না।
“শয়তান তোমাদেরকে দারিদ্র্যের কথা বলে ভয় দেখায় এবং অশ্লীল কর্মকাণ্ড করতে প্রলোভিত করে। কিন্তু আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা ও অনুগ্রহের আশা প্রদান করেন”- (বাকারাহঃ ২৬৮)।
বৈধ-অবৈধ উপায়ে অঢেল সম্পদের মালিক যারা, তাদের কাছে কোন মহৎ কাজের জন্যে, ইসলামের সমুন্নতির জন্যে, ওয়াজ মাহফিল, সীরাত মাহফিল, ইসলামী সম্মেলন, পাপাচার-অনাচার বন্ধের জন্যে অর্থ সাহায্য চাইলে তারা অক্ষমতা প্রকাশ করে। অথচ তারা ছেলেমেয়ের বিয়ে-শাদীর জন্যে, নাচ-গান ও বিভিন্ন অপসংস্কৃতির প্রচার ও প্রসারের জন্যে, নৈতিক মেরুদণ্ড ধ্বংসকারী অশ্লীল ও যৌন উত্তেজক ছায়াছবির জন্যে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করতে কোন কুণ্ঠাবোধ করে না। এ সবকিছুই জাহেলিয়াতের চিন্তাধারা ও মনমানসিকতার ফসল। তাদের সকল চেষ্টা-চরিত্র এবং চাওয়া-পাওয়া দুনিয়ার জীবনকে কেন্দ্র করেই। তারা দুনিয়ায় যা পেতে চায় তার সবটুকু না হলেও অনেক কিছুই আল্লাহ তাদেরকে দেন। কিন্তু আখিরাতে তাদের প্রাপ্য কিছুই থাকে না। স্বয়ং আল্লাহতায়ালা একথা কুরআনে ঘোষণা করেছেন।
অপরদিকে জাহেলিয়াতের মুকাবিলায় ইসলাম জীবন সম্পর্কে ধারণা ও দৃষ্টিভংগি সম্পূর্ণ পরিবর্তন করে দেয়। দুনিয়া ও আখিরাতের জীবন মিলেই মানুষের পূর্ণাংগ জীবন। দুনিয়ার জীবন আখিরাতের জীবনের কর্মক্ষেত্র। দুনিয়ার জীবনের কর্মফলই আখিরাতে মানুষ ভোগ করবে। আখিরাতের জীবনকে সুখী ও সুন্দর করার জন্যে ইসলাম পরিপূর্ণ কর্মসূচি পেশ করেছে এবং প্রতিটি কর্মে আখিরাতকে প্রাধান্য দিতে হবে। এ বিশ্বাস যার পাকাপোক্ত সে আখিরাতের জন্যেই তার দুনিয়ার জীবন, তার ধন-সম্পদ সবকিছুই বিলিয়ে দেবে। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে এ বিশ্বাস ও তার ভিত্তিতে মন-মানসিকতা ও চরিত্র তৈরি হয়েছিল। ইসলামের জন্যে যখন যে ধরনের ত্যাগের প্রয়োজন হয়েছে, তাঁরা অকাতরে সে ত্যাগের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। নবম হিজরীতে লক্ষাধিক রোমীয় সৈন্যের নব-প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্রের উপর আক্রমণের সংবাদে নবী (সা) যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। তবুক প্রান্তরে শত্রুর মুকাবিলা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
যুদ্ধের জন্যে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। তার জন্যে নবী আহবান জানালেন। জিহাদের প্রেরণা তীব্রতর করার জন্যে কুরআন-এর সূরার কিয়দংশ নাযিল হলো। সাহাবীদের মধ্যে অর্থ ও যুদ্ধের উপকরণ সরবরাহের প্রতিযোগিতা শুরু হলো। হযরত ওমর (রা) তাঁর সমুদয় সম্পদ দু’ভাগ করে এক ভাগ জিহাদ ফান্ডে দান করলেন। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) তাঁর সর্বস্ব এনে হাজির করলেন। তা দেখে নবী (সা) বললেন, ‘মা আবকায়তা লে আহলিকা ইয়া আবা বাকার?’ ‘আবু বকর! তোমার পরিবারের জন্যে কি রেখেছ?’
“আমার পরিবারের জন্যে আল্লাহ ও তাঁর রসূল ছাড়া আর কিছুই নেই”- অম্লান মুখে জবাব দিলেন সিদ্দীকে আকবর (রা)।
এই হলো ইসলামের মহান শিক্ষা, চরিত্র ও ত্যাগ। তারা দুনিয়ার জীবনও সামগ্রিকভাবে বিলিয়ে দিয়েছেন আখিরাতের জীবনের জন্যে।
ইসলামের একরূপতা ও একমুখীনতা
ইসলামের মেজাজ-প্রকৃতি হচ্ছে একেবারে একমুখো। সকল দিক, সকল আদর্শ, মতবাদ ও দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মুখ ফিরিয়ে আল্লাহমুখী হওয়াই ইসলামের দাবি। ইসলাম ও তার অনুসারীদের চিন্তা-চেতনা ও কর্মে একই রং ও সাদৃশ্য দেখতে চায় যা তাদের মধ্যে এক বিশেষ স্বাতন্ত্র্য-স্বকীয়তা সৃষ্টি করবে। বাইরের কোন আকীদা-বিশ্বাস, চিন্তাধারা ও ধ্যান-ধারণার কোন সামান্যতম সংমিশ্রণ ইসলাম বরদাশত করে না। সে এতোটা সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরি মনে করে যে, সে জাহেলিয়াতপন্থীদের ওসব রসম-রেওয়াজ ও আচার-অনুষ্ঠানও গ্রহণ ও পালনের অনুমতি দেয় না, যার মধ্যে শির্ক-কুফর ও পাপাচারের কোন কিছু দেখা যায় না। যা শুধু গতানুগতিক বা প্রচলিত ধারার অনুবর্তী। ভিন্ন জাতির কোন কিছু বলে অথবা কোন জিদের বশবর্তী হয়ে এ সতর্কতা অবলম্বন করা হচ্ছে তা নয়। বরঞ্চ দ্বীনের একটা বিশেষ তাৎপর্য, উদ্দেশ্য ও দূরদর্শিতার জন্যে এ সতর্কতা অবলম্বন অপরিহার্য হয়ে পড়ে। তাৎপর্য এই যে, ইসলামের অনুসারীদের চিন্তা ও কাজের দিক দিয়ে একমাত্র আল্লাহমুখী হওয়ার প্রবণতা যেন সংরক্ষিত থাকে। এমনটি যেন না হয় যে, জাহেলিয়াতের ছোটোখাটো কোন নির্দোষ বস্তু অনুকরণ করা হলো, এবং পরবর্তীকালে এ অনুকরণপ্রিয়তা জাহেলিয়াতের চিন্তাধারার অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে গোমরাহির পথ প্রশস্ত করে দিল। এ আশংকা কোন কাল্পনিক আশংকা নয় বরঞ্চ বাস্তব। মানবীয় মনস্তত্ত্ব ও অভিজ্ঞতা অতীতে এর বহু দৃষ্টান্ত পেশ করেছে।
এ এমন এক গূঢ় তত্ত্ব যে সাধারণতঃ মানুষের অন্তর্দৃষ্টি সেখানে পৌঁছতে পারে না। এমন কি কতিপয় সাহাবায়ে কেরামের পক্ষ থেকেও এ বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বনের দৃষ্টান্ত আছে। হযরত আবু ওয়াকেদ লায়সী (রা) বলেন, নবী করীম (সা) যখন হুনায়েনের সিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন, তখন মুসলিম সেনাবাহিনীকে একটি বিশেষ গাছের পাশ দিয়ে যেতে হয়েছিল যাকে ‘যাতে-আনওয়াত’ বলা হতো। একথা প্রচলিত ছিল যে, মুশরিকগণ এ গাছে তাদের অস্ত্রশস্ত্র লটকিয়ে রাখতো। তা দেখে কতিপয় মুসলমান বললেন, “হে আল্লাহর রসূল! মুশরিকদের যেমন ‘যাতে আনওয়াত’ রয়েছে, তেমনি আমাদের জন্যে একটি ‘যাতে আনওয়াত’ নির্ধারিত করে দিন।”
নবীর সংগী-সাথী সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে কেউ কেউ মনে করেছিলেন- নবী (সা) তাঁদের জন্যে যে কোন একটি গাছ নির্দিষ্ট করে দিলে তার উপরে তাঁদের যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম ও অস্ত্রশস্ত্র ঝুলিয়ে রাখবেন। এটাকে তারা দূষণীয় মনে করেননি। এ কাজের মধ্যে শির্ক-কুফরেরও কোন গন্ধ ছিল না। এসব চিন্তা করেই তাঁরা নবীকে উপরোক্ত অনুরোধ জানান। তাঁদের এ ধরনের চিন্তায় কোন ত্রুটি ছিল বলেও তো মনে করা যায় না। কিন্তু নবীর সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি এ সম্ভাবনা দেখতে পেয়েছিল যে এভাবে মুসলমানদের মধ্যে এমন এক মানসিকতা সৃষ্টি হতে পারে যে, জাহেলিয়াতের ভ্রান্ত চিন্তাধারা থেকে যতোটা পরিচ্ছন্ন থাকা দরকার তা আর থাকবে না। দ্বীনের যে আল্লাহমুখী মেজাজ প্রকৃতি তার সাথে এ ধরনের আবেদনের কোন মিল দেখা যায় না। এ কারণেই নবী পাক (সা) তাঁদের আবেদনের জবাবে বলেন, “সুবহানাল্লাহ! এতো ঠিক সেই ধরনের কথা যেমন মুসার (আ) লোকজন তাঁকে বলেছিল- আমাদের জন্যেও একটি প্রতিমা বানিয়ে দাও, যেমন তাদের অনেক প্রতিমা রয়েছে।” তিরমিযী শরীফে এ ঘটনা বিবৃত করা হয়েছে।
বনী ইসরাঈলের উপরোক্ত আবেদন এবং নবীর সাহাবীদের আবেদনের মধ্যে তো মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। তথাপি তাদের সাথে এদের আবেদনকে একইরূপ মনে করার কারণ এ ছাড়া আর কিছু ছিল না যে, এ আবেদনের পেছনে যে মানসিকতা ছিল তা ক্রমশঃ বিশ্বাসমূলক ও বাস্তব কুফল বয়ে আনতে পারে এবং জাহেলিয়াতপন্থীদের দৃশ্যতঃ একটা নির্দোষ ও সাদাসিধে প্রচলন-পদ্ধতির অনুসরণ জাহেলিয়াতের চিন্তাধারা ও কর্মকাণ্ড অনুসরণের প্রবণতা সৃষ্টি করতে পারে। এজন্যে দূরদর্শী ও সূক্ষ্মদর্শী নবী উপরোক্ত কথা বলার পর এ আশংকা করে ভবিষ্যদ্বাণীও করেন। তিনি বলেন-
“সেই সত্তার কসম যাঁর মুষ্ঠির মধ্যে আমার জীবন, তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তীদের আচরণ অনুসরণ করবে”- (তিরমিযী)।
নবীর এ ভবিষ্যদ্বাণীতে ‘তোমরা’ বলতে সাহাবায়ে কেরামকে বুঝানো হয়নি, পরবর্তীকালের মুসলমানদের বুঝানো হয়েছে। ‘পূর্ববর্তীদের’ বলতে বুঝানো হয়েছে ইহুদী ও খৃস্টানদেরকে। নবী পাক (সা) এ কথাই বলতে চেয়েছেন- আজ তো আমি তোমাদেরকে এ চিন্তার ভ্রান্তি ও তার ভয়াবহ পরিণাম থেকে রক্ষা করব। কিন্তু ভবিষ্যতে যখন মুসলমানদের ঈমানী অনুভূতি দুর্বল হয়ে পড়বে; তখন জাহেলিয়াতের প্রভাব বাড়তে থাকবে। ফলে যেভাবে ইহুদী ও নাসারা জাহেলিয়াতের অনুপ্রবেশের পথ উন্মুক্ত করতে থাকে, মুসলমানরাও তা-ই করবে।
মুসলমানদের ঐক্য ও পরামর্শভিত্তিক সিদ্ধান্ত
জাহেলিয়াতের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করে পুরোপুরি ইসলামের পথে চলার জন্যে মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য অপরহার্য। ঐক্যবদ্ধভাবেই জাহেলিয়াতের মুকাবিলা করতে হবে। তারই জন্যে মুসলমানদের জামায়াতবদ্ধ জীবন ফরয করে দেয়া হয়েছে। কুরআন ও হাদীসে এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট নির্দেশ দেয়া হয়েছে।
আল্লাহ বলেন- “সকলে মিলে আল্লাহর রশি শক্ত করে ধর এবং দলাদলিতে লিপ্ত হয়ো না”- (আলে ইমরানঃ ১০৩)।
এখানে রশি অর্থে আল্লাহর দ্বীনকে বুঝানো হয়েছে। দ্বীনকে রশির সমতুল্য করে এজন্যে বর্ণনা করা হয়েছে যে, এ দ্বীনের রশি দিয়ে একদিক দিয়ে যেমন ঈমানদারগণকে আল্লাহর সাথে বেঁধে দেয়া হয় অর্থাৎ আল্লাহর সাথে তাদের গভীর-নিবিড় সম্পর্ক সৃষ্টি করে দেয়া হয়, ঠিক তেমনি অপরদিক দিয়ে এটি সকল ঈমানদারকে পরস্পরের সাথে একাত্ম করে দেয় এবং তাদেরকে গভীর ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করে দেয়। তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করে একটি জামায়াত বানিয়ে দেয়। মুসলমানদের জীবনের লক্ষ্য যেহেতু ইকামাতে দ্বীন অর্থাৎ দ্বীন কায়েম করা ও কায়েম রাখা, সেজন্যে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা ও সংগ্রামের মাধ্যমেই তা করা সম্ভব। আর এ কাজ করতে হলে জাহেলিয়াতের মুকাবিলা করে, তাকে জীবনের সকল ক্ষেত্র থেকে উচ্ছেদ করেই করতে হবে। তাই জামায়াতবদ্ধ হয়ে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম অপরিহার্য।
দ্বীনকে বা দ্বীনের রশিকে শক্ত করে ধরার অর্থ এই যে, মুসলমানের দৃষ্টিতে প্রকৃত গুরুত্ব দ্বীনের। এর প্রতিষ্ঠার জন্যে এবং প্রতিষ্ঠার পর তা অক্ষুণ্ণ ও অমলিন রাখার জন্যেই তার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চলবে। এ কাজের জন্যে একে অপরকে সাহায্য করবে। কিন্তু দ্বীনের মৌলিক শিক্ষা ও তার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য থেকে যদি মুসলমান সরে পড়ে, ছোটো-খাটো ও অপ্রয়োজনীয় বিষয় নিয়ে মতানৈক্য সৃষ্টি করে, তাহলে পূর্ববর্তী উম্মাতদের মতো তারা দলে উপদলে বিভক্ত হওয়ার পর জীবনের মূল লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে দুনিয়া ও আখিরাতে চরম লাঞ্ছনার শিকার হবে। ঐক্য বিনষ্ট করে দলে-উপদলে বিভক্ত হলে জাহেলিয়াত তথা বাতিল শক্তি তার প্রভাব ও কর্তৃত্ব বিস্তার করতে সক্ষম হয়। তাই বাতিলের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের নির্দেশই আল্লাহ দিয়েছেন।
নবী মুহাম্মাদের (সা) নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের মাধ্যমে ইসলামের রাষ্ট্রীয় প্রাসাদ সুপ্রতিষ্ঠিত হলেও পরবর্তীকালে মুসলমানদের পারস্পরিক মতভেদ ও মতানৈক্যের কারণে তা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়- সে আলোচনা পরে করা হবে।
ইসলামী জামায়াত গঠন, জামায়াতের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এবং জামায়াত থেকে বেরিয়ে যাওয়ার ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে হাদীসে বিশদ বর্ণনা দেখতে পাওয়া যায়।
ইসলামী জামায়াত, সমাজ ও রাষ্ট্রকে পতনের হাত থেকে রক্ষা করার জন্যে মুসলমানদের অন্যান্য বহু ঈমানী গুণাবলীর সাথে আর একটি বিষয়ের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে এবং তা হলো পরামর্শভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ। কুরআন পাকে এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট নির্দেশ দেয়া হয়েছে।
জামায়াত, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত গৃহীত না হলে, নেতৃত্বের প্রতি অনাস্থা সৃষ্টি হয়, অনৈক্য ও দলাদলির পথ প্রশস্ত হয়। এজন্যে পরামর্শভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।
কুরআন বলে, “(হে নবী!) তুমি তাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি উপেক্ষা কর; তাদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং দ্বীনের কাজকর্মে তাদের সাথে পরামর্শ কর”- (আলে ইমরানঃ ১৮৯)।
কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে, “এবং যারা তাদের রবের ডাকে সাড়া দেয় (রবের প্রতিটি হুকুম মেনে চলে), এবং নামায কায়েম করে এবং নিজেদের কাজকর্ম পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে সম্পন্ন করে”- (শুরাঃ ৩৮)।
পারস্পরিক আলাপ-আলোচনা ও পরামর্শ করে কাজ করাকে এখানে ঈমানের সর্বোৎকৃষ্ট গুণাবলীর মধ্যে শামিল করা হয়েছে। উপরে বর্ণিত সূরা আলে ইমরানেও এর নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ কারণে পরামর্শভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণকে ইসলামী জীবন পদ্ধতির গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। বিনা পরামর্শে কোন এক ব্যক্তির অথবা বিশেষ দল ও গোষ্ঠীর খুশি-খেয়াল মতো কাজ করা শুধু জাহেলিয়াতের রীতি-পদ্ধতিই নয়; বরং আল্লাহতায়ালার নির্ধারিত রীতি-পদ্ধতির একেবারে পরিপন্থীও।
পরামর্শভিত্তিক কাজের উপর এতোটা গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে কেন তা গভীরভাবে চিন্তা করলে তিনটি বিষয় সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।
একটি হচ্ছে এই যে, যে বিষয়ের সাথে দুই বা ততোধিক ব্যক্তির স্বার্থ জড়িত, সে বিষয়ে কোন এক ব্যক্তির খেয়াল-খুশি মতো সিদ্ধান্ত করে ফেলা এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করা নিঃসন্দেহে অন্যায় এবং অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি। সামষ্টিক ও বহু ব্যক্তি সম্পর্কিত কার্যকলাপে কারো স্বেচ্ছাচারিতার অধিকার থাকতে পারে না। যে বিষয়ের সাথে বহু মানুষের স্বার্থ জড়িত, তাদের সকলের স্বাধীন মতামত গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয় এবং ইনসাফ তা-ই দাবি করে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সংখ্যা যদি খুব বিরাট হয়, তাহলে তাদের আস্থাভাজন প্রতিনিধিগণকে পরামর্শে শরীক করাই বাঞ্ছনীয়।
দ্বিতীয় এই যে, একমাত্র সে ব্যক্তিই সামগ্রিক সামষ্টিক ব্যাপারে অন্যান্যের সাথে পরামর্শ না করে আপন স্বেচ্ছাচারিতা চালাতে চায়, যে শুধু নিজের স্বার্থ হাসিল করতে চায়। পরামর্শ না করার পেছনে তার এ মানসিকতা কাজ করে যে, সে নিজেকে সকলের চেয়ে বড়ো ও বুদ্ধিমান মনে করে এবং অপরকে তুচ্ছ ও পরামর্শের অযোগ্য মনে করে। এ হচ্ছে জাহেলিয়াতের সৃষ্ট মানসিকতা তথা ইবলিশী মানসিকতা। একজন ঈমানদার লোক এমন স্বার্থপর হতে পারে না যে, অপরের অধিকারে হস্তক্ষেপ করে নিজের স্বার্থ হাসিল করবে এবং এ গর্ব অহংকারও করতে পারে না যে সে-ই একমাত্র বুদ্ধিমান ও সবজান্তা। আর যতসব বুদ্ধিহীন ও গাধা-গর্দভ। একজন মুমিন এমন ধরনের চিন্তাও করতে পারে না।
তৃতীয় এই যে, যেসব বিষয় অপরের অধিকার ও স্বার্থের সাথে সংশ্লিষ্ট, সেসবের ফয়সালা করা এক বিরাট দায়িত্ব। আর ইসলামের সুস্পষ্ট ঘোষণা যে, যার উপরে যে দায়িত্ব অর্পিত আছে, তাকে তার জন্যে অবশ্যই আখিরাতে খোদার কাছে জবাবদিহি করতে হবে যে, সে সঠিকভাবে তার দায়িত্ব পালন করেছে কিনা। অতএব যে ব্যক্তি খোদাকে ভয় করে এবং মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে যে, খোদার সামনে তাকে কত কঠিন জবাবদিহি করতে হবে, তাহলে সে এতো কঠিন দায়িত্বের বোঝা স্বেচ্ছায় মাথায় নেয়ার দুঃসাহস করতে পারে না। এমন কাজ তো সে-ই করতে পারে যে না খোদাকে ভয় করে আর না আখিরাতে জবাবদিহির কোন পরোয়া করে। যার মধ্যে খোদার ভয় এবং আখিরাতে জবাবদিহির অনুভূতি আছে সে অবশ্যই চেষ্টা করবে যে, একটি বিষয়ের সাথে যে যে ব্যক্তির স্বার্থ জড়িত তাদের সবাইকে অথবা তাদের মনোনীত প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিবর্গকে সে বিষয়ে ফয়সালা করার আলোচনায় শরীক করবে যাতে সঠিক ও ইনসাফপূর্ণ সিদ্ধান্তে পৌঁছা যায়।
উপরের তিনটি বিষয় সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করলে এ কথা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, ইসলাম যে ধরনের চরিত্রবান লোক তৈরি করতে চায় এবং তাদের মাধ্যমে সমাজে যে ইনসাফ কায়েম করতে চায় তার জন্যে পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ একান্ত অপরিহার্য দাবি। এ দাবি পূরণ না করা জাহেলিয়াতেরই চরিত্র। ইসলামী জীবন ব্যবস্থার দাবিই এই যে, প্রত্যেকটি ছোটো বড়ো সামগ্রিক-সামষ্টিক ব্যাপারই পারস্পরিক আলোচনার ভিত্তিতে সমাধা করতে হবে। সমাজের সর্বস্তরেই এ নীতি পালন করতে হবে। পারিবারিক ব্যাপার হলে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে এবং পুত্রগণ প্রাপ্তবয়স্ক হলে তাদেরকেও আলোচনায় অংশীদার করতে হবে। গোত্রীয় ও মহল্লার ব্যাপারে হলে এবং সকলের সম্মিলিতভাবে আলোচনা সম্ভব না হলে সকলের সম্মিলিত ও গ্রহণযোগ্য পদ্ধতিতে নির্বাচিত ও নির্ভরযোগ্য পঞ্চায়েত বা প্রতিনিধিবর্গের মাধ্যমে সমাধান করবে। কোন সম্প্রদায়ের (COMMUNITY) ব্যাপার হলে তা পরিচালনা করার জন্যে সম্প্রদায়ের সকলের অথবা নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের স্বাধীন মতামতের ভিত্তিতে কারো উপরে দায়িত্ব অর্পিত হবে। তখন সে ব্যক্তি সকলের সাথে অথবা তা সম্ভব না হলে তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সাথে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। সে ব্যক্তির নেতৃত্ব বা তার উপর অর্পিত দায়িত্ব ততোক্ষণ পর্যন্ত চলবে যতোক্ষণ লোক তার উপর আস্থা পোষণ করতে থাকবে। আস্থা বিনষ্ট হলে তাকে নেতৃত্ব থেকে অপসারণও করতে পারবে। কোন ঈমানদার ব্যক্তি বলপ্রয়োগে নেতা হতে বা নেতা থাকার চেষ্টা করতে পারে না। এমন ধরনের ধোঁকাও সে দিতে পারে না যে, বল প্রয়োগে জাতির নেতৃত্ব দখল করলো এবং জুলুম করে জাতির সমর্থন আদায় করলো। সে এমন ধরনের চালবাজিও করতে পারে না যে, জনগণ তাদের মর্জিমতো স্বাধীনভাবে পরামর্শ পরিষদের (শূরা বা পার্লামেন্ট) সদস্য নির্বাচন করতে পারলো না, বরং ক্ষমতা দখলকারী ব্যক্তির পছন্দ অনুযায়ী করল। ইসলামের নির্ধারিত পন্থা-পদ্ধতি পরিহার করে বলপ্রয়োগ ও ধোঁকা-প্রতারণার আশ্রয় সে ব্যক্তিই নিতে পারে যার মনে খোদার ভয় ও আখিরাতে জবাবদিহির কোন অনুভূতি নেই।
এ নীতি নবী পাক (সা) স্বয়ং মেনে চলতেন। তাঁর নিকটে আল্লাহর ওহীর মাধ্যমে সুস্পষ্ট নির্দেশ আসতো। আল্লাহর সুস্পষ্ট নির্দেশ তো প্রশ্নাতীত। সে সম্পর্কে কোন পরামর্শ বা আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। তবে নির্দেশ কিভাবে, কোন পদ্ধতিতে, কোন পরিবেশে কার্যকর করা হবে সে সম্পর্কে আলোচনা ও পরামর্শের প্রয়োজন দেখা দিতে পারে এবং এরূপ ক্ষেত্রে নবী মুস্তাফা তা করেছেন। নবীর পরে খোলাফায়ে রাশেদার যুগেও এ নীতি পুরোপুরি মেনে চলা হয়েছে।
জাহেলিয়াতের পুনরুত্থান
ইসলাম ও জাহেলিয়াতের দ্বন্দ্ব-সংঘাত যেহেতু চিরস্থায়ী ও চিরকালীন সেজন্যে জাহেলিয়াত ইসলামের দ্বারা পরাজিত ও পরাভূত হওয়ার পর পুনরায় ধীরে ধীরে মাথাচাড়া দিয়ে উঠবার অব্যাহত চেষ্টা করতে থাকে। আল্লাহতায়ালা মানুষকে জাহেলিয়াতের প্রভাব থেকে মুক্ত করে তাকে জীবনের সঠিক পথে চালাবার জন্যে যুগে যুগে নবী-রসূল প্রেরণ করেছেন। তাঁরা মানুষের চিন্তাধারা, আকীদাহ-বিশ্বাস, স্বভাব-চরিত্র ও আচার-আচরণ জাহেলিয়াতের প্রভাব থেকে মুক্ত ও পরিচ্ছন্ন করে আল্লাহর মনোনীত পথে পরিচালিত করে জীবনকে সুখী ও সুন্দর করেন। মানুষ তাদের নেতৃত্বে পরিশুদ্ধ জীবন যাপন করতে থাকে। কিন্তু তাঁদের তিরোধানের পর তাঁদের আদর্শ ও শিক্ষা থেকে মানুষ ধীরে ধীরে দূরে সরে যেতে থাকে এবং জাহেলিয়াত তাদেরকে নানান ভ্রান্তির বেড়াজালে আবদ্ধ করে গোমরাহ করার সুযোগ লাভ করে। তারপর গোটা মানব সমাজ জাহেলিয়াতের অক্টোপাসে আবদ্ধ হয়ে যায়। যতোদিন নবীগণের আদর্শ ও নীতিমালা মানুষ আঁকড়ে ধরে থাকে ততোদিন জাহেলিয়াত আত্মগোপন করে সুযোগের সন্ধানে থাকে এবং বার বার সত্যনিষ্ঠ ও সত্যপন্থীদের মনে অসআসা (প্ররোচনা) সৃষ্টি করতে থাকে। এ প্ররোচনা সৃষ্টিকারী স্বয়ং ইবলিস শয়তান, তার অসংখ্য অগণিত অনুসারী জ্বিন ও মানুষ এবং স্বয়ং মানুষের নফস বা কুপ্রবৃত্তি। এ প্ররোচনার তীর বার বার নিক্ষিপ্ত হতে থাকে এবং একাধিকবার লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ার পর সঠিক স্থানে পৌঁছে যায় এবং জাহেলিয়াতের পুনরুত্থান শুরু হয়।
অবশ্যি এসব প্ররোচনাদানকারীদের প্ররোচনা থেকে আল্লাহ তার কাছে আশ্রয় প্রার্থনার জন্যে মানুষকে নির্দেশ দিয়েছেন। এ নির্দেশ উপেক্ষা করার ফলে এবং নানাবিধ পার্থিব স্বার্থের কারণে মানুষ প্ররোচনার শিকার হয়ে পড়ে। এভাবে জাহেলিয়াত তার গোমরাহীর সকল হাতিয়ারসহ সামনে অগ্রসর হয়।
ইতিহাস এ কথার সাক্ষী যে, সপ্তম শতকের প্রথমার্ধেই প্রথম ইসলামের সার্বিক বিজয় সূচিত হয়েছিল তা নয়। বরঞ্চ এর আগেও বার বার ইসলামের স্বর্ণযুগ এসেছে। কারণ এ এক ঐতিহাসিক সত্য যে, খোদার বান্দাহদেরকে সত্যপথ দেখাবার জন্যে বার বার নবী-রসূলগণ দুনিয়ায় তশরিফ এনেছেন। তাঁরা এমন অবস্থায় দুনিয়া ত্যাগ করেন যখন জাহেলিয়াত সত্যের কাছে মাথানত করেছে। কিন্তু কিছুকাল পর জাহেলিয়াত তার অশুভ তৎপরতা শুরু করে এবং মানুষ ক্রমশঃ বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট হয়ে শির্ক ও কুফরে লিপ্ত হয়ে পড়ে। বনী ইসরাঈলের ইতিহাসেও এ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। হযরত মুসা আলায়হিস সালাতু ওয়াসসালামের পর তাঁর সুযোগ্য ও সত্যনিষ্ঠ খলিফা ইউশা বিন নূনের জীবনকালে এবং তারপরও কিছুকাল যাবত আল্লাহর দ্বীন মানুষের জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত ছিল যার কারণে বিশ্ববাসীর উপর তাদেরই শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল। এ কথার উল্লেখ করে কুরআন পাকে বলা হয়েছে- “হে বনী ইসরাঈলগণ! স্মরণ কর তোমাদের প্রতি আমাদের দেয়া নিয়ামতকে। আর এ কথাও স্মরণ কর যে, আমি তোমাদেরকে দুনিয়ার জাতিসমূহের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছিলাম”- (সূরা বাকারাহঃ ৪৭, ১২২)।
কিন্তু পরবর্তীকালে যখন তাদের দ্বীনী প্রাণশক্তি নিস্তেজ হয়ে পড়ে এবং চিন্তা, চরিত্র ও আচরণে বিকৃতি পরিস্ফুট হতে থাকে, তখন জাহেলিয়াত তাদের উপর সর্বশক্তি দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারপর অবস্থা এমন হয়ে পড়ে যে, বনী ইসরাঈল জাহেলিয়াতের মধ্যে একাকার হয়ে যায়। এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে, জাহেলিয়াত অবস্থার প্রেক্ষিতে নীরবতা অবলম্বন করলেও তা সাময়িক; রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করে না- শুধু সুযোগের প্রতীক্ষায় থাকে। জাহেলিয়াতের উৎস যেহেতু স্বয়ং ইবলিস শয়তান, এবং বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহতায়ালার বিশেষ হিকমত ও ইচ্ছার দরুন এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে শয়তান কিয়ামত পর্যন্ত জীবিত থাকবে, সে জন্যে সত্য ও মিথ্যার, মঙ্গল ও অমঙ্গলের দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ চিরকাল চলতে থাকবে। এ দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ প্রকৃতপক্ষে মানুষের পরীক্ষার জন্যে এবং এ জন্যেই তার সৃষ্টি।
অতএব কিয়ামত পর্যন্ত ইবলিস শয়তানের চিরজীবী হওয়ার কারণে অতীতের সকল নবীর উম্মাতের সাথে সে যে আচরণ করেছে, পরবর্তীকালে ইসলাম ও উম্মাতে মুসলেমার প্রতি তার আচরণ তা-ই হওয়াই অতি স্বাভাবিক।
এ সম্পর্কে নবী মুহাম্মাদ (সা) ভবিষ্যদ্বাণীও করেছেন। তিনি বলেন, “তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের পদে পদে অনুসরণ-অনুকরণ করবে। এমনকি তারা যদি গোসাপের গর্তে প্রবেশ করে থাকে, তোমরাও তা-ই করবে।” সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করেন, “হে আল্লাহর রসূল! পূর্ববর্তী লোকদের বলতে কি ইহুদী-নাসারা বুঝায়?” তিনি বলেন, “তাছাড়া আর কে?”- (বুখারী)।
নবীপাকের উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণীর অর্থ ছিল এই যে, দুনিয়ার ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক মঞ্চে যেসব জাতি উল্লেখযোগ্য তাদের সাথে স্বাভাবিকভাবেই তোমাদের সংযোগ সম্পর্ক স্থাপিত হবে। তারপর যতোদিন তোমাদের ঈমানের দৃঢ়তা অম্লান থাকবে ততোদিন তোমরা তাদের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার পরিবর্তে তাদেরকেই প্রভাবিত করতে থাকবে। ফলে মুসলমানরা পদে পদে তাদের অনুসরণ করা শুরু করবে। তাদের রীতিনীতি, চিন্তা-পদ্ধতি, আচার-অনুষ্ঠান তোমরা অবলম্বন করতে থাকবে। পথভ্রষ্ট জাতি ও পাপাচারী সম্প্রদায়ের আনুগত্য করতে কোন দ্বিধাবোধ করবে না। এসব হওয়ার পর স্বাভাবিকভাবেই তারা তাদের স্বাতন্ত্র্য-স্বকীয়তা ও দ্বীনী আত্মসচেতনতা সংরক্ষণ করতে পারবে না। অতঃপর চিন্তা-চেতনা, আচার-আচরণ ও যাবতীয় কর্মকাণ্ডের দিক দিয়ে ইসলাম ও জাহেলিয়াতের মধ্যে যে দুর্ভেদ্য প্রাচীর তৈরি করে রাখা হয়েছিল যার সংরক্ষণ দ্বীন ও ঈমান সংরক্ষণের মতোই অত্যাবশ্যক ছিল- তা স্থানে স্থানে ধসে পড়তে থাকবে এবং মুসলমান তাদের জাতীয় স্বাতন্ত্র্য ও পরিচয় হারিয়ে ফেলবে।
জাহেলিয়াতের চতুর্মুখী হামলা
জাহেলিয়াত তার পরাজয়ের গ্লানি মুছে ফেলে দিয়ে পুনরায় মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। শুধু তা-ই নয়, সে পূর্ণশক্তি দিয়ে ইসলামের উপর চতুর্মুখী হামলা চালায়। তার হামলা ছিল দ্বীনী আকীদাহ-বিশ্বাসের উপর, ইসলামী শরিয়তের উপর, ইসলামের মূলনীতি ও ধ্যান-ধারণার উপর এবং মুসলমানের জাতীয় ঐক্যের উপর। তার সর্বপ্রথম লক্ষ্য ছিল ইসলামের মৌল আকীদাহ-বিশ্বাস। যে বুনিয়াদের উপর গোটা দ্বীনী প্রাসাদ প্রতিষ্ঠিত তা ধ্বংস করতে পারলে অন্যান্য ধ্যান-ধারণা, হেদায়েত ও হুকুম-আহকাম সহজেই নির্মূল করা যায়। সে একটি একটি করে ইসলামের মৌল বিষয়গুলোর উপর তার আক্রমণ জোরদার করে।
নবুওতের উপর বিশ্বাস
তাওহীদের প্রতি বিশ্বাস ছিল জাহেলিয়াতের জন্যে একেবারে অসহনীয়। কিন্তু প্রথমেই তার উপর আক্রমণ করার কোন পথ তার ছিল না। অতএব তার আক্রমণের সূচনা হয় নবুওতে মুহাম্মাদীর আকীদাহর উপর থেকে। অর্থাৎ নবুওতে মুহাম্মাদীর বিশ্বাসকে যদি নড়বড়ে অথবা বিনষ্ট করা যায় তাহলে ইসলামের অন্যান্য মৌল বিশ্বাসগুলি মন থেকে মুছে ফেলা সহজ হবে। এ উদ্দেশ্যে জাহেলিয়াত কয়েকটি রণক্ষেত্র তৈরি করে।
প্রথম রণক্ষেত্র ছিল মিথ্যানবী গঠনের। অর্থাৎ শেষনবী মুহাম্মাদ (সা)-এর পরও মিথ্যা নবুওতের দাবিদারগণের আবির্ভাব হতে থাকবে। এর প্রস্তুতি যদিও নবী মুহাম্মাদ (সা)-এর জীবদ্দশাতেই চলছিল, কিন্তু তাঁর ওফাতের পর এ তৎপরতা জোরদার হয় এবং মুসায়লামা ও আসওয়াদুল আনাসী নামক দুই ব্যক্তিকে নবুওতের দাবিদার হিসেবে পেশ করা হয়। বনী হানিফা গোত্রসহ কতিপয় লোক মুসায়লামাকে এবং ইয়েমেনবাসী আসওয়াদুল আনাসীকে সমর্থন করে। কিন্তু প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) সর্বশক্তি দিয়ে এ ফেৎনার মূলোৎপাটন করেন।
অতঃপর খেলাফতে রাশেদার শেষের দিকে শিয়া ফের্কার আবির্ভাব ঘটে এবং পরবর্তীতে তা যখন বহু দলে উপদলে বিভক্ত হয় তখন তাদের মধ্য থেকে মিথ্যা নবীর আবির্ভাব ঘটতে থাকে। যেমন তাদের মনসূরীয়া ফের্কার প্রতিষ্ঠাতা আবু মনসূর ঘোষণা করে- “হযরত আলী (রা) আল্লাহর রসূল ও নবী ছিলেন। তারপর হযরত হাসান (রা), হুসাইন (রা), আলী ইবনে হুসাইন এবং মুহাম্মাদ বিন আলী সকলে রসূল ও নবী ছিলেন। আমিও একজন রসূল ও নবী এবং আমার পর ছয় পুরুষ পর্যন্ত নবুওতের ধারাবাহিকতা চলতে থাকবে।”
সে আরও বলে যে, নবুওতের ধারাবাহিকতা কখনো শেষ হবে না- (আল মিলালে ওয়ান নিহালে, শাহরাস্তানী)।
খাত্তাবিয়া ফের্কার প্রতিষ্ঠাতা আবু খাত্তাব বলে, শিয়াদের সকল ইমাম নবী। মুগিরিয়া ফের্কার প্রতিষ্ঠাতা মুগিরা স্বয়ং নবুওতের দাবিদার ছিল। নূসাইরিয়া ফের্কার নেতা মুহাম্মাদ বিন নাসীরুন নুসাইরীও নবুওতের দাবি করে- (উপরোক্ত গ্রন্থ)। তাদের এসব দাবির সমর্থনে কোন যুক্তি নেই, প্রমাণ নেই, কোন খোদাপ্রদত্ত সনদ নেই। দরকারই কি? যুক্তি-প্রমাণের প্রশ্ন তুললেই তো গোলমাল, সব ভেস্তে যাওয়ার কথা। শুধু প্রয়োজন দুর্বল ঈমান ও বিকৃত মানসিকতার মুসলমানদের মধ্যে এক ধর্মীয় উন্মাদনা সৃষ্টি করা। আর পেছনে থাকবে শয়তানের প্রবল প্ররোচনা ও প্রতারণা।
এসব মিথ্যা নবুওতের দাবিদারকে সাধারণভাবে প্রত্যাখ্যান করা হলেও মুষ্টিমেয় কিছু লোক তো অবশ্যই বিভ্রান্ত হয়েছে। জাহেলিয়াতের পাতানো ফাঁদে পড়ে বিভ্রান্ত হয়েছে, পথভ্রষ্ট হয়েছে।
এ হচ্ছে জাহেলিয়াতের নব অভিযানের একশ’ দেড়শ’ বছরের ঘটনা। হয়তো মুসলিম জগতের কোথাও কোথাও এ ধরনের আরও ঘটনা ঘটে থাকতে পারে। বিশেষ করে মুসলমানদের পতনযুগে এ ধরনের ঘটনা সংঘটিত হওয়া খুবই স্বাভাবিক এবং তা ঘটেছেও। মুসলমানরা যখন তাওহীদ রিসালাত ও আখিরাতের মৌল বিশ্বাস থেকে কিছুটা সরে পড়ে, জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর আনুগত্য ও রসূলের নেতৃত্ব পরিহার করে তাগুতি শক্তির কাছে মাথা নত করে তখন জাহেলিয়াত তার পূর্ণশক্তি নিয়ে মুসলমানদের আকীদাহ-বিশ্বাসের উপর চরম আঘাত হানে এবং পুরোপুরি না হলেও আংশিক বিজয় লাভ করে।
নতুন ধর্মের প্রবর্তন
ভারতের বাদশাহ আকবর ইসলাম নির্মূল করার উদ্দেশ্যে ‘দ্বীনে ইলাহী’ নামে এক উদ্ভট ধর্ম প্রবর্তনের চেষ্টা করেন। ইসলামের বিকল্প হিসেবেই এ নতুন ধর্মটি চালু করাই ছিল আকবরের ইচ্ছা। এ নতুন ধর্ম প্রবর্তনের পেছনে তার যে মানসিকতা কাজ করছিল তা এই যে, ভারতের মতো বিশাল ভূখণ্ডে তার শাসন স্থায়ী ও মজবুত করতে হলে এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের মন অবশ্যই জয় করতে হবে। ধর্মের হাতিয়ার দিয়ে তাদের মন জয় করা তিনি সমীচীন মনে করেন। সেজন্যে তার প্রচেষ্টা ছিল সকল ধর্মের সমন্বয়ে এক নতুন ধর্মের প্রবর্তন। এ নতুন ধর্মে ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলি পরিহার করা হয় এবং হিন্দু ধর্মের বহু আচার-অনুষ্ঠান মুসলমানদের জন্যে বাধ্যতামূলক করা হয়। যেমন মুসলমানরা তাদের চিরাচরিত মুসলিম নাম রাখতে পারবে না, পুত্রসন্তানদের খাৎনা করাতে পারবে না, দাড়ি রাখা যাবে না, গরুর গোশত খাওয়া যাবে না। মুসলমান-অমুসলমানের মধ্যে অবাধে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করা যাবে এবং তার জন্যে কোন অমুসলমানকে ইসলাম গ্রহণ করতে হবে না।
মজার ব্যাপার এই যে, এ ধর্মের অধীনে হিন্দু, জৈন, বৌদ্ধ প্রভৃতি সকল ধর্মাবলম্বীগণ তাদের স্ব স্ব ধর্ম যথাযথভাবে পালন করতে পারতো। শুধু ইসলামী শরিয়তের বহু বিধি-বিধান রহিত করা হয়। ইসলাম বিলোপ সাধনের উদ্দেশ্যেই যে এ ধর্মের আবিষ্কার করা হয় তা অতি সুস্পষ্ট।
আকবরের প্রতি অমুসলিম জনগোষ্ঠী অতিমাত্রায় তুষ্ট হয়েছিল বটে, কিন্তু তারাও এ ধর্ম গ্রহণ করতে রাজি হয়নি। অবশ্য মুষ্টিমেয় সুবিধাবাদী ও পথভ্রষ্ট মুসলমান এ ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়। বৃহত্তর মুসলিম জনগোষ্ঠী এ ধর্ম প্রত্যাখ্যান করে। তৎকালীন প্রসিদ্ধ আলেম ও তাপস শায়খ আহমদ সিরহিন্দী মুজাদ্দিদে আলফেসানী (রাহ) এ নতুন ধর্ম প্রচারের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেন। আকবরের মৃত্যুর পর তার পুত্র জাহাঁগীর ‘দ্বীনে ইলাহী’ ধর্মের ধারক ও বাহক সেজে তা প্রবর্তনের আপ্রাণ চেষ্টা করেন। আলফেসানীকে গোয়ালিয়র দুর্গে কারারুদ্ধ করে এবং তার সকল রাষ্ট্রশক্তি প্রয়োগ করেও এ উদ্ভট ধর্মটির অপমৃত্যু রোধ করতে পারেননি। অবশেষে তিনি তার গদি রক্ষার জন্যেই আলফেসানীকে মুক্তি দান করেন এবং তাঁর কাছে তাওবা করে নতুন করে মুসলমান হন। আকবর তার নিজের তথা মোগল শাসন স্থায়ী ও সুদৃঢ় করার জন্যে যে কৌশল অবলম্বন করেন তা মোগল সাম্রাজ্যের পতনের বীজ বপন করেছিল।
মিথ্যা নবীর পুনরাবির্ভাব
ভারতের ব্রিটিশ শাসন আমলে মির্জা গোলাম আহমদের মিথ্যা নবুওতের এক ষড়যন্ত্র-জাল বিস্তার করা হয়। এ ষড়যন্ত্রে সর্বতোভাবে সাহায্য করে ব্রিটিশ সরকার। বড় বড় সরকারি চাকুরি, পদোন্নতি ও বিভিন্ন অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধার প্রলোভন ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ বহু মুসলমানকে প্রতারিত ও পথভ্রষ্ট করে। রাষ্ট্রের ছত্রছায়ায় খ্রিস্টান মিশনারীদের ব্যাপক তৎপরতা মুষ্টিমেয় মুসলমানকেই মাত্র খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করতে পেরেছে। কিন্তু মিথ্যা নবুওতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের ফলে যে এক নতুন নবী ও নতুন মুসলমান সম্প্রদায় আবিষ্কার করা হলো তার দ্বারা একদিকে কুরআনের সত্যতা অস্বীকার করা হলো এবং এ নতুন নবীর অবিশ্বাসকারীকে কাফির বলে ঘোষণা করা হলো। এ জাহেলিয়াতের এক সাময়িক কৃতিত্ব সন্দেহ নেই। কিন্তু দুনিয়ার প্রায় সকল মুসলিম দেশ বিদেশী ও বিধর্মী শক্তির উপনিবেশে পরিণত হলেও এবং বিপুলসংখ্যক মুসলমান ইসলামী আচার-আচরণ থেকে দূরে সরে থাকলেও সামগ্রিকভাবে মুসলিম মিল্লাত মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর মিথ্যা নবুওতের দাবি ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে।
মির্জা গোলাম আহমদ পূর্ব পাঞ্জাবের কাদিয়ান নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন বলে তার অনুসারীদেরকে কাদিয়ানী বলে অভিহিত করা হয়। তাদেরকে আহমদীয়াও বলা হয়। এ শতাব্দীর প্রথম পাদেই বিশ্বের আলেম সমাজের পক্ষ থেকে কাদিয়ানী বা আহমদীয়া সম্প্রদায়কে অমুসলিম বা কাফির বলে ঘোষণা করা হয়। এ নবুওতকে মিথ্যা ও প্রতারণামূলক প্রমাণিত করে বহু প্রামাণ্য গ্রন্থও রচিত হয়। অতঃপর ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের ফলে স্বাধীন পাকিস্তান রাষ্ট্র কায়েম হওয়ার পর এ মিথ্যা নবুওতের বিরুদ্ধে জোরদার আন্দোলন শুরু হয়। আরব দেশগুলোতে তাদের প্রচারণা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। অবশেষে ১৯৭৪ সালে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে কাদিয়ানী সম্প্রদায়কে অমুসলিম ঘোষণা করে আইন পাস করা হয়।
শির্ক ফিন্নবুওত
ইসলামের বিরুদ্ধে জাহেলিয়াতের প্রথম রণক্ষেত্র (WAR FRONT) তৈরি হয়েছিল মিথ্যা নবুওতের দাবি নিয়ে। এ দাবি বিভিন্ন যুগে করা হয়েছে। জাহেলিয়াতের দ্বিতীয় রণক্ষেত্র হলো শির্ক ফিন্নবুওতের। অর্থাৎ নবুওতের মধ্যে অংশীদারিত্বের এক উদ্ভট আকীদাহ-বিশ্বাস আবিষ্কার করা হয়। এ জন্য সর্বপ্রথম হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহুর সত্তাকে বিশেষভাবে আবরণরূপে ব্যবহার করা হয়। এ ছিল ইসলামী ইতিহাসের এক অতি বেদনাদায়ক ঘটনা যে, খিলাফত সম্পর্কিত অবাঞ্ছিত বিতর্ক মুসলিম মিল্লাতকে দ্বিধাবিভক্ত করে শিয়া নামে একটা স্থায়ী ফের্কার উদ্ভব হয়। এ ফের্কার অন্তর্ভুক্ত লোক এ ধারণা-বিশ্বাসকে তাদের ঈমানের অংগ-অংশ বলে গ্রহণ করেন যে, নবী মুহাম্মাদ মুস্তাফা (সা) হযরত আলীকে (রা) তাঁর প্রতিনিধি ও খলিফা হিসেবে অসিয়ত করে যান। এর চেয়ে অধিকতর বেদনাদায়ক ব্যাপার এই যে, তারা হযরত আলী (রা) সহ তাদের ইমামগণকে নিষ্পাপ বলে বিশ্বাস করেন। মুসলমানদের এ যাবত মৌল আকীদা-বিশ্বাস এ ছিল যে, মানবজাতির মধ্যে শুধুমাত্র নবীগণ নিষ্পাপ এবং এ নিষ্পাপ হওয়ার কৃতিত্ব তাঁদের নিজেদের নয়। বরঞ্চ আল্লাহ তাঁদেরকে মানবগোষ্ঠীর মধ্য থেকে নবুওতের মহান কাজের জন্যে বেছে নিয়েছেন বলে তিনি তাঁর বিশেষ অনুগ্রহে তাঁদেরকে নিষ্পাপ রেখেছেন। এখন নবী ব্যতীত অন্য কাউকে নিষ্পাপ গণ্য করলে নবী ও অ-নবীর মধ্যে যে মৌলিক পার্থক্য তা আর থাকে না।
শিয়াদের মনে এ বিশ্বাস পাকাপোক্ত হয় যে, শুধু হযরত আলী (রা) নন, বরঞ্চ তাঁর বংশোদ্ভূত সকল ইমাম ঠিক তেমনি নিষ্পাপ ছিলেন যেমন নিষ্পাপ ছিলেন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা)। নবুওত সম্পর্কিত ইসলামী আকীদার পরিপন্থী জাহেলিয়াতের এ এক বিরাট কৃতিত্ব। কারণ আহলে বায়ত বা নবী পরিবারের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধার অতিশয়োক্তি শির্ক ফিন্নবুওতের পর্যায়ে পৌঁছে যায়। কোন অ-নবীকে নিষ্পাপ মনে করার অর্থ তাকে প্রকৃতপক্ষে নবুওতের পদমর্যাদা ও অধিকারে সমমর্যাদা দান করা। অতঃপর রিসালাতে মুহাম্মাদীর আকীদা আর ইসলামী আকীদা থাকে না। ফলে সে মহান উদ্দেশ্য হাসিলের কোন আশা করা যায় না যার জন্যে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এ বিশ্বজনীন ও চিরন্তন রিসালাতের মর্যাদা কায়েম করেছিলেন এবং নবী মুহাম্মাদকে (সা) সর্বশেষ নবী হিসেবে পাঠিয়েছিলেন। কারণ এমতাবস্থায় তিনি (নবী মুস্তাফা) একাকী হেদায়েতের উৎস ও একমাত্র স্বীকৃত হকের মাপকাঠি আর রইলেন না। আর শর্তহীন আনুগত্যের অধিকারও তাঁর জন্যে নির্দিষ্ট রইলো না। বরঞ্চ তারাও এসব ব্যাপারে নবীর সমমর্যাদা লাভ করেছেন যাদেরকে নিষ্পাপ মনে করা হচ্ছে।
খিলাফত থেকে রাজতন্ত্র
খিলাফতে রাশেদা উচ্ছেদ করে রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা জাহেলিয়াতের বিরাট বিজয়। চতুর্থ খলিফা হযরত আলীর (রা) শাহাদাতের পর রাজতন্ত্রের পথ সুগম হয় এবং হযরত মুয়াবিয়ার (রা) ইসলামী রাষ্ট্রের ক্ষমতা দখলের সাথে সাথে খিলাফতে রাশেদার পতন হয়।
খিলাফতে রাশেদার পতনকে জাহেলিয়াতের বিরাট বিজয় এ জন্যে বলা হয় যে, খিলাফতে রাশেদা নিছক একটা রাজনৈতিক শক্তি বা সরকার ছিল না, বরঞ্চ তা ছিল নবুওতে মুহাম্মাদীর পরিপূর্ণ প্রতিনিধিত্ব। তার কাজ শুধু এতোটুকু ছিল না যে, দেশের আইন-শৃংখলা পরিচালনা করবে, শান্তি-নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত করবে ও সীমান্ত রক্ষা করবে। বরঞ্চ তা মুসলমানদের সামষ্টিক জীবনে শিক্ষক, মুরব্বী ও পথপ্রদর্শকের সেসব দায়িত্ব পালন করতো যা নবী করীম (সা) তাঁর জীবদ্দশায় পালন করে যাচ্ছিলেন। খিলাফতের দায়িত্ব এটাও ছিল যে, দারুল ইসলামের মধ্যে দ্বীনে হকের গোটা ব্যবস্থাকে তার প্রকৃত আকার-প্রকৃতি ও প্রাণশক্তিসহ প্রাণবন্ত রাখবে এবং দুনিয়ার মুসলমানদের সামগ্রিক শক্তি আল্লাহর কালেমা বুলন্দ করার কাজে নিয়োজিত রাখবে। হযরত উসমান যুন্নুরাইন রাদিআল্লাহু আনহুর খিলাফতের আমলে কিভাবে খিলাফতে রাশেদার পতনের প্রক্রিয়া শুরু হয় এবং হযরত আলীর (রা) খিলাফতের পর তা রাজতন্ত্রে পরিণত হয়- এ দীর্ঘ ইতিহাস বর্ণনা করার অবকাশ এখানে নেই। ইতিহাসের ছাত্র মাত্রেরই তা জানা থাকার কথা। তবে খিলাফতে রাশেদার অবসানের পর ইসলামের বিরুদ্ধে অধিকতর রণক্ষেত্র তৈরি করা জাহেলিয়াতের জন্যে সহজ হয়ে পড়ে।
খিলাফতে রাশেদার পর
খিলাফতে রাশেদার অবসানের পর রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়, (যদিও তাকে খিলাফত নামেই অভিহিত করা হয়) সেখানে ইসলামী আদর্শ ও মূলনীতি পরিহার করে চলা হয়। নবী মুহাম্মাদ মুস্তাফা (সা) যে একটি পরিপূর্ণ ইনসাফভিত্তিক সমাজব্যবস্থা কায়েম করেন তা খিলাফতে রাশেদার যুগে অমলিন ও অবিকৃৎ রইলেও রাজতন্ত্রের অধীনে তার আর কোন অস্তিত্ব রইলো না। ইসলামের জনকল্যাণকর শাসনের পরিবর্তে বলপ্রয়োগে আনুগত্যের স্বীকৃতি আদায় করা হয়। মানুষের স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করার আর কোন সুযোগই রইলো না এবং স্বাধীন মত ব্যক্ত করতে গিয়ে অনেককে জীবনও দিতে হয়।
এ কথা সত্য যে, রাজতন্ত্রের অধীনে দেশের পর দেশ বিজিত হয়। রাষ্ট্রের পরিধি বর্ধিত হয়। কিন্তু ইসলামের পরামর্শভিত্তিক সিদ্ধান্তের পরিবর্তে এক ব্যক্তির মর্জিমতো সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার ফলে মুসলমানদের মধ্যে চিন্তার ঐক্য বিনষ্ট হয় এবং তারা বহু দল-উপদলে বিভক্ত হতে থাকে। ইসলাম-বিরোধী আদর্শ ও চিন্তাধারা তাদেরকে প্রভাবিত করতে থাকে।
খিলাফতে রাশেদা তথা কুরআন ও সুন্নাহর শাসন রহিত হওয়ার পর মুসলিম সমাজ ও মন-মানসে, চিন্তা ও চরিত্রে বিকৃতি শুরু হয়। ইসলামী জ্ঞান ও চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তিগণ রাজতন্ত্রের অধীনে কোন সরকারি দায়িত্ব পালনে অনীহা প্রকাশ করেন এবং সমাজের দৃশ্যপট থেকে সরে পড়েন।
উল্লেখ্য যে, নবী মুস্তাফার দ্বারা পূর্ণাংগ ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হওয়ার সাথে সাথে দলে দলে লোক ইসলামের পতাকাতলে আশ্রয় গ্রহণ করে। অতঃপর তাদের অনেকেই তাদের জীবন পরিশুদ্ধ করার সুযোগই পায়নি। নবী পাকের সাক্ষাৎ লাভের ভাগ্যও অনেকের হয়নি।
নবী পাকের ইন্তেকালের পর হযরত আবু বকর (রা) ও হযরত উসমান (রা)- এর খিলাফতকালে ইসলামী দাওয়াত ও বিজয় অব্যাহত থাকে। এ সময়ের মধ্যে বিভিন্ন দেশ, অঞ্চল, জাতি ও শ্রেণীর অসংখ্য লোক তাদের পূর্বপুরুষদের ধর্মত্যাগ করে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করে। তারা সাধারণতঃ ইসলামকে সত্য দ্বীন হিসেবে মনে-প্রাণে মেনে নেয়। কিন্তু তাদের মধ্যে অনেক এমনও ছিল, যাদের ইসলাম গ্রহণের পেছনে কোন সদিচ্ছা ছিল না। তারা অন্তরে ইসলামের জন্যে মর্মজ্বালা ভোগ করতো এবং ইসলামের প্রতি প্রতিহিংসা ও শত্রুতা পোষণ করতো। ইসলামের উপর চরম আঘাত হানার সুযোগসন্ধানী তারা ছিল। তারা তাদের এ অসৎ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্যে নিজেদেরকে মুসলমানের দলে শামিল করে নেয়। তারা ছিল প্রকৃতপক্ষে মুনাফিক। জনৈক ইহুদী আলেম আব্দুল্লাহ ইবনে সাবা ছিল তাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সে ইসলামের নামে মুসলিম মিল্লাতকে দ্বিধাবিভক্ত করে এবং তাদের মধ্যে এক পৃথক আকীদাহ-বিশ্বাস, চিন্তাধারা ও আচার-আচরণ প্রবর্তন করতে সক্ষম হয়।
রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর কর্তৃত্বের চাবিকাঠি ইসলামের পরিবর্তে জাহেলিয়াতের হাতে চলে যায়। আর রাষ্ট্রক্ষমতা হাতছাড়া হওয়ার পর জাহেলিয়াতের অগ্রগতি রোধ করার শক্তি ইসলামের ছিল না। তাছাড়া ইসলামের জন্যে জাহেলিয়াতের মুকাবিলা করা বড় কঠিন ছিল এ জন্যে যে, জাহেলিয়াত তার আসল রূপ নিয়ে ময়দানে অবতীর্ণ না হয়ে বরং ‘মুসলমান’-এর রূপ নিয়েই অবতীর্ণ হয়। জাহেলিয়াত ইসলামের প্রকাশ্য দুশমন হিসেবে নাস্তিক, কাফির বা মুশরিকের রূপ ধারণ করে ইসলামের উপর আঘাত হানতে এলে গোটা মুসলিম মিল্লাত ঐক্যবদ্ধ হয়ে তার মুকাবিলা করতো। কিন্তু জাহেলিয়াতের মুখে ছিল তাওহীদ-রিসালাতের স্বীকৃতি এবং সে যা কিছু করতো তা ইসলামেরই নামে। ইসলামের আবরণেই জাহেলিয়াত তার শিকড় মজবুত করতে থাকে।
জাহেলিয়াত রাষ্ট্র ও সম্পদ করায়ত্ত করে তার নাম দেয় খিলাফত। কিন্তু আসলে তা ছিল রাজতন্ত্র যা খতম করাই ছিল ইসলামের লক্ষ্য। এ রাজতন্ত্রের ছত্রছায়ায় শাসকগোষ্ঠী, তাদের অধীন আমীর-ওমরাহ, গভর্নর, সেনাবাহিনী ও সমাজের কর্তৃত্বশালী ব্যক্তিদের জীবনে জাহেলিয়াতের চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গি বিস্তার লাভ করে। সেই সাথে জাহেলিয়াতের দর্শন, সাহিত্য এবং শিল্পকলাও বিস্তার লাভ করতে থাকে।
জাহেলিয়াত যেহেতু রাষ্ট্রশক্তির অধিকারী হয় সে জন্যে ওলামা, সুফী ও খোদাভীরু লোকদের উপরও প্রভাব বিস্তার করে। ফলে মুসলিম সমাজে প্লেটোর দর্শন, বৈরাগ্যবাদী চারিত্রিক আদর্শ এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রে নৈরাশ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গি প্রসার লাভ করে।
সমাজের চরিত্রবান লোকদেরকে তাকওয়া পরহেজগারীর নামে সমাজের কর্তৃত্ব-নেতৃত্ব থেকে সরিয়ে দিয়ে জাহেলিয়াতের পতাকাবাহীদের হাতে ক্ষমতা তুলে দেয়।
অনৈসলামী তাসাউফ
উপরে বর্ণিত হয়েছে যে, ইসলামের বিরুদ্ধে জাহেলিয়াতের প্রথম ও দ্বিতীয় রণক্ষেত্র তৈরি হয়েছিল মিথ্যা নবুওতের ও নবুওতের অংশীদারিত্বের দাবিতে। এ দু’টি ফ্রন্টের প্রথমটিতে জাহেলিয়াত জয়লাভ করতে না পারলেও দ্বিতীয়টিতে তার প্রাধান্য বিস্তার লাভ করে মুসলিম মিল্লাতের ঐক্য বিনষ্ট করে এবং ইসলামী খিলাফতের প্রাসাদকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে। অতঃপর প্রতিষ্ঠিত রাজতন্ত্রের ছত্রছায়ায় জাহেলিয়াত তার কালো হাত বিস্তার করতে থাকে। যে সকল সৎ ও খোদাভীরু লোক পরিস্থিতির চাপে রাজনৈতিক অঙ্গন থেকে সরে গিয়ে তাসাউফ তথা আত্মশুদ্ধি, জিকির-আজকার ও দ্বীনী ইলমের চর্চা ও শিক্ষাঙ্গনে নিজেদেরকে নিয়োজিত রাখেন, সেখানেও জাহেলিয়াত তার প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। ফলে ইসলামভিত্তিক তাসাউফের মুকাবিলায় জাহেলী তাসাউফের আবির্ভাব ঘটে। এ ছিল ইসলামের বিরুদ্ধে জাহেলিয়াতের তৃতীয় WAR FRONT বা রণক্ষেত্র।
এ জাহেলী তাসাউফ নবুওতের আকীদাহ বিশ্বাসকেই মন থেকে মুছে ফেলতে চাইছিল। এ তাসাউফের বুনিয়াদী চিন্তা ছিল এই যে, যে বন্দেগীর লক্ষ্য খোদা পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়া, তার জন্যে না কোন নবীর মধ্যস্থতার প্রয়োজন আছে, আর না তাঁর আনুগত্যের প্রয়োজন। এ ছাড়াও লোক এ মনজিলে মকসূদে পৌঁছতে পারে। সম্ভবতঃ এ বাতিল তাসাউফপন্থীগণ একটি শিয়া ফের্কা থেকে এ চিন্তা-ধারণা গ্রহণ করে। কাইয়ালিয়া নামক শিয়া ফের্কাটির প্রতিষ্ঠাতা আহমদ বিন আল কাইয়ালের বক্তব্য এই যে, যাদের মধ্যে অন্তর্দৃষ্টির অভাব তারাই নবীগণের অন্ধ অনুসারী হয়।
এ চিন্তাধারাকে একটু পালিশ করে এভাবেই বলা হয়ঃ হাকিমের দরবারে নিজের আরজ পেশ করার জন্যে যেমন কোন উকিলের মধ্যস্থতা অপরিহার্য ঠিক তেমনি খোদার দরবারে বান্দার পক্ষ থেকে কিছু পেশ করতে হলে পীরের মধ্যস্থতা অপরিহার্য। এভাবে বান্দা ও খোদার মধ্যে নবীর মধ্যস্থতা অর্থাৎ নবীর আনুগত্যের মাধ্যমেই খোদার আনুগত্য এবং খোদা প্রাপ্তির যে সহজ-সরল রাজপথ নবী দেখিয়ে দিয়েছেন- সে নবীর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে পীরের আনুগত্যকেই একমাত্র খোদা প্রাপ্তির মধ্যস্থতা মনে করা হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বান্দার সকল আনুগত্য পীর পর্যন্তই সীমিত হয়ে থাকে এবং আনুগত্যের ধারণা তার ঊর্ধ্বে উঠতে পারে না। ফলে হালাল-হারাম, ভালো-মন্দ এবং বন্দেগী ও নাফরমানীর মাপকাঠি একমাত্র পীর হয়ে পড়ে। এভাবে খোদা ও নবীর সাথে বান্দার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়।
এ চিন্তাধারা ও দর্শন যদি গ্রহণ করা হয় তাহলে ‘নবুওতে মুহাম্মাদী’ কেন ‘ঈমান বির রিসালাত’ই অনাবশ্যক হয়ে পড়ে। ইসলাম, কুরআন ও নবীর উপর বিশ্বাস স্থাপনকারী কেউ কি অমন ধরনের চিন্তা-ধারণা পোষণ করতে পারে? কিন্তু চরম দুঃখজনক ব্যাপার এই যে, জাহেলিয়াত এ ভ্রান্ত চিন্তাধারার মারাত্মক রোগ এক শ্রেণীর মুসলমানদের মধ্যে সংক্রমিত করেছে এবং ইসলামের নামেই এক শ্রেণীর লোক এ চিন্তার ধারক-বাহক ও প্রচারক সেজেছে।
উল্লেখ্য যে, ইসলামসম্মত তাসাউফ ও তাসাউফপন্থীদের অস্তিত্ব সমাজে বিদ্যমান থাকলেও তাঁদের সংখ্যা অতি নগণ্য। বাতিল তাসাউফপন্থীদের অধীনে শরিয়তের কোন অনুশাসন মেনে চলার প্রয়োজন হয় না বিধায় সুবিধাবাদীর দল এদিকেই বেশি ঝুঁকে পড়ে। জাহেলিয়াতের প্রচার প্রোপাগান্ডাও এর স্বপক্ষে বড়ো জোরদার।
জাহেলিয়াতের মারাত্মক অস্ত্র
জাহেলী তাসাউফ কিছুসংখ্যক মুসলমানকে বিভ্রান্ত করে ইসলামের সত্য-সঠিক ও সহজ-সরল রাজপথ (সিরাতুল মুস্তাকীম) থেকে যে বিচ্যুত করেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু পরবর্তীকালে জাহেলিয়াতের অতি মারাত্মক তিনটি অস্ত্র ইসলামের মূল বুনিয়াদকেই নড়বড়ে করে দিয়েছে। সে তিনটি হচ্ছে (১) খোদাহীন বা খোদাদ্রোহী জীবনব্যবস্থা (SECULARISM) (২) জাতিপূজা তথা জাতীয়তাবাদ (NATIONALISM) এবং (৩) সার্বভৌমত্বের দাবিদার গণতন্ত্র (DEMOCRACY)। এ তিনটি মারাত্মক অস্ত্র সম্পর্কে আলোচনা করলে বুঝা যাবে যে, এগুলো ইসলামী বিশ্বাস ও চিন্তা-চেতনাকে কতখানি প্রভাবিত করেছে এবং ইসলামের পরিপন্থী জীবনদর্শন ও মতবাদ কতটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
সেকিউলারিজম
প্রথমে SECULARISM (সেকিউলারিজম) সম্পর্কে আলোচনা করা যাক। এর মর্ম হচ্ছে, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিশ্বস্রষ্টার বিধান ও পথ-নির্দেশনা প্রত্যাখ্যান করে নিজেদের রচিত বিধান ও পথ নির্দেশনা অনুযায়ী জীবন যাপন করা। তবে অত্যন্ত চতুরতার সাথে বলা হয়, কারো বিবেক যদি এ সাক্ষ্য দেয় যে, খোদা বলে কেউ আছেন এবং তাঁর স্তবস্তুতি করা উচিত, তাহলে সে তার ব্যক্তিগত জীবনে তা করতে পারে। কিন্তু দুনিয়া, সমাজ ও তৎসম্পর্কিত যাবতীয় ব্যাপারে খোদা ও ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই। এ তত্ত্বের ভিত্তিতে যে জীবনব্যবস্থার প্রাসাদ গড়ে উঠেছে তার মধ্যে মানুষের সাথে মানুষের এবং মানুষের সাথে দুনিয়ার সম্পর্কের সকল স্তর খোদা ও ধর্ম থেকে একেবারে স্বাধীন। গোটা সমাজব্যবস্থা ধর্ম থেকে স্বাধীন, শিক্ষাব্যবস্থা স্বাধীন, আইন-কানুন স্বাধীন, দেশের পার্লামেন্ট স্বাধীন, রাজনীতি, অর্থনীতি, দেশের যাবতীয় ব্যবস্থাপনা এবং আন্তর্জাতিক সম্বন্ধ-সম্পর্ক সবই খোদা ও ধর্ম থেকে স্বাধীন; মানব জীবনের এসব বিভিন্ন দিক ও বিভাগে যে সিদ্ধান্তই করা হয়ে থাকে তাতে এ প্রশ্ন অবান্তর, মূলতঃ অর্থহীন এবং অন্ধ কুসংস্কারাচ্ছন্ন চিন্তাপ্রসূত যে, খোদা এসব ব্যাপারে কোন মূলনীতি ও নির্দেশ আমাদের জন্যে নির্ধারিত করে দিয়েছেন কিনা। আর দিয়ে থাকলেও অবস্থা ও পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে তা মেনে চলা সম্ভব নয়। এখন রইলো ব্যক্তিগত জীবন। কিন্তু ধর্মহীন শিক্ষাব্যবস্থা ও সামাজিকতার প্রভাবে ব্যক্তিগত জীবনও অধিকাংশ ক্ষেত্রে ধর্মবিবর্জিত হয়ে পড়েছে এবং পড়ছে। কারণ এখন অতি অল্পসংখ্যক লোকের মন এ সাক্ষ্য দেয় যে, খোদা বলে কেউ আছেন এবং তাঁর হুকুম মেনে চলতে হবে। বিশেষ করে এ সেকিউলারিজমের ভিত্তিতে যে সমাজ-সভ্যতা গড়ে উঠেছে, তার কর্ণধার যারা তাদের জন্যে ধর্ম এখন ব্যক্তিগত জীবনের ব্যাপারও আর নেই। খোদার সাথে তাদের আপন সম্পর্কও ছিন্ন হয়েছে।
এ সেকিউলারিজম তথা ধর্মহীনতা বা খোদাদ্রোহীতার জন্ম ইউরোপে এবং এর একটা পশ্চাৎ পটভূমিও (BACKGROUND) রয়েছে। সংক্ষেপে হলেও তার আলোচনা ব্যতীত বিষয়টি উপলব্ধি করা কষ্টকর হবে বলে মনে হয়।
খৃস্টান পাদ্রীগণ বিকৃত খৃস্টবাদের ভিত্তিতে নিজেদের মনগড়া শরিয়ত বা ধর্মীয় বিধি-বিধান রচনা করেন এবং ধর্মের নামে শাসন চালাতে থাকেন। সমাজ পরিচালনার উপযোগী শরিয়তের বিধান তাওরাতে ছিল। ইহুদী আলেমগণ তাওরাতকে যথাসম্ভব বিকৃত করলেও মূল তাওরাতকেই খৃস্টানগণ প্রত্যাখ্যান করেন। বাইবেলের মাধ্যমে কোন নতুন শরিয়ত নাযিল করা হয়েছিল না। ফলে খৃস্টান পাদ্রীগণ তাদের নিজেদের স্বার্থে ধর্মকে বিকৃত করে ধর্মের নামে শাসনকার্য পরিচালনা করতে থাকেন। খোদা প্রেরিত আইনের পরিবর্তে মানুষের মনগড়া আইনের দ্বারা সমাজে শান্তি, নিরাপত্তা ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা কিছুতেই সম্ভব ছিল না। এ শাসনের অধীনে অনাচার-অবিচার, জুলুম-নির্যাতন চলতে থাকলেও তার উপর ধর্মের ছাপ থাকায় সাধারণ মানুষ তা অগত্যা নীরবে মেনে নিত। গোটা ইউরোপে পাদ্রীদের দ্বারা পরিচালিত বহু ছোটো-বড়ো রাজ্য ছিল যেগুলোকে PAPAL STATES বলা হতো। এ সবের উপর এক খৃস্টীয় সাম্রাজ্য কায়েম করা হয়েছিল যাকে বলা হতো HOLY ROMAN EMPIRE।
উল্লেখ্য, অষ্টম শতাব্দীর সূচনালগ্নে স্পেনে মুসলিম শাসন কায়েম হয় এবং কয়েকশ’ বছর সে শাসন বলবৎ থাকে (৭১১-১৪৯২ খৃঃ)। মুসলিম শাসন আমলে কর্ডোভা ও গ্রানাডায় সর্ববৃহৎ দু’টি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয় এবং ইউরোপের বিভিন্ন স্থান থেকে জ্ঞানপিপাসু মানুষ জ্ঞানলাভের জন্যে দলে দলে এসব সুউচ্চ বিদ্যাপীঠে ভিড় করতে থাকে। উচ্চশিক্ষায় এসব প্রতিষ্ঠান ইউরোপে জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকবর্তিকা প্রজ্জ্বলিত করে। তদানীন্তন বিশ্বে বাগদাদ, কর্ডোভা এবং কস্তুনতানিয়া (CONSTANTINOPLE) ছিল সমগ্র বিশ্বের মধ্যে শিক্ষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতির কেন্দ্রভূমি। কিন্তু কর্ডোভার স্থান ছিল সকলের উচ্চে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চায় কর্ডোভার (CORDOVA) খ্যাতি ছিল বিশ্ববিখ্যাত। ব্যাপক জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার ফলে শিক্ষিত সমাজের মধ্যে মুক্ত ও স্বাধীন চিন্তার উন্মেষ ঘটে। সেইসাথে বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কারও হতে থাকে। পাদ্রীদের জীর্ণ পুরাতন কুসংস্কারাচ্ছন্ন চিন্তা-চেতনার সাথে বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার প্রচণ্ড সংঘর্ষ শুরু হয়। বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা ও আবিষ্কার বন্ধ করার জন্যে নতুন নতুন আইন প্রণয়ন করা হয়। আইন অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ও লোমহর্ষক শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়। যেহেতু এ সবকিছু ধর্মের দোহাই দিয়েই করা হচ্ছিল, সেজন্যে শিক্ষিত সমাজ ধর্মের প্রতিই বীতশ্রদ্ধ হতে থাকে।
প্রাচীনকালের খৃস্টান পণ্ডিত ও দার্শনিকগণ তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস এবং মানুষ ও বিশ্ব প্রকৃতি সম্পর্কিত ধারণার গোটা প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন গ্রীকদর্শন ও বিজ্ঞানের ধারণা-মতবাদ, যুক্তি-প্রমাণ ও তথ্যাদির উপর। তাদের এ ধারণাও ছিল যে, যেসব বুনিয়াদের উপর তাদের মতবাদের প্রাসাদ নির্মিত, তার কোন একটির উপর যদি আঘাত আসে, তাহলে গোটা প্রাসাদই চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। সেইসাথে খৃস্টান ধর্মও শেষ হয়ে যাবে। গ্রীকদর্শন ও বিজ্ঞানের সর্বস্বীকৃত সত্যের প্রতি সন্দেহ সৃষ্টিকারী কোন সমালোচনা ও গবেষণা তারা কিছুতেই বরদাশত করতে রাজি ছিলেন না। এমন কোন দার্শনিক চিন্তাধারাও তারা মেনে নিতে প্রস্তুত ছিলেন না, যা এসব সর্বস্বীকৃত সত্যকে পরিহার করে অন্য কোন চিন্তা পেশ করতো, যার কারণে পাদ্রী সম্প্রদায় তাদের দর্শন পুনর্বিবেচনার প্রয়োজন বোধ করতো। এমন কোন গবেষণা কাজেরও অনুমতি দেয়া যেতো না যার দ্বারা মানুষ ও বিশ্বপ্রকৃতি সম্পর্কে বাইবেলে উপস্থাপিত ধারণা এবং দার্শনিকদের গৃহীত ধারণা মতবাদের কোন অংশ ভুল প্রমাণিত হতে পারতো। এ ধরনের প্রতিটি বিষয়কে তারা ধর্মের জন্য এবং তার উপর প্রতিষ্ঠিত গোটা সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার জন্যে প্রত্যক্ষ বিপদ মনে করতেন। পক্ষান্তরে যারা রেঁনেসা আন্দোলন ও তার দাবি অনুযায়ী সমালোচনা, গবেষণা ও তথ্যানুসন্ধানের কাজ করছিলেন, তাদের প্রতিটি পদক্ষেপে সেসব দর্শন ও বিজ্ঞানের দুর্বলতা সুস্পষ্ট হয়ে ধরা পড়তো যে সবের ভিত্তিতে ধর্মীয় বিশ্বাসের গোটা প্রাসাদ তৈরি করা হয়েছিল। কিন্তু তারা যতোই গবেষণার ক্ষেত্রে অগ্রসর হচ্ছিলেন, ততোই পদ্রী বা খৃস্টান সম্প্রদায় তাদের ধর্মীয় বা রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রয়োগ করে দিন দিন কঠোরতার সাথে তাদের পথ রুদ্ধ করার চেষ্টা করতো। পূর্ববর্তীকালের বহু স্বীকৃত সত্যের পরিপন্থী বহুকিছু দিবালোকের মতো স্পষ্ট চোখে পড়তো। পাদ্রী সম্প্রদায় বলতো, সর্বস্বীকৃত সত্যাবলী পুনর্বিবেচনা করার পরিবর্তে সমালোচকদের চক্ষু উৎপাটিত করে দিতে হবে। গবেষকদের কাছে মনে হতো, যেসব মতবাদকে ধর্মীয় বিশ্বাসের অখণ্ডনীয় দলিল-প্রমাণ মনে করা হতো, তার মধ্যে বিস্তর ত্রুটি রয়েছে। পাদ্রী সম্প্রদায় বলতো, যাদের মন-মস্তিষ্কে এ ধরনের চিন্তার উদ্রেক হয় তাদের মস্তিষ্কই চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিতে হবে। এ দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষের পরিণাম ছিল এই যে, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তিক নবজাগরণের প্রথম প্রভাতেই ধর্ম ও ধার্মিকদের বিরুদ্ধে একগুঁয়েমির মনোভাব সৃষ্টি হয় এবং নতুন সভ্যতার শিরা-উপশিরায় খোদা-বিমুখতা এবং ধর্মহীনতার মানসিকতা সংক্রমিত হয়। অতঃপর এসব স্বাধীন চিন্তার প্রবক্তাগণের কাছে এটা আশা করা যেতো না যে, তারা অন্যান্য ধর্মকে গির্জার খৃস্ট ধর্ম থেকে পৃথক করে দেখবেন। এজন্যে স্বাভাবিকভাবেই তাদের এ একগুঁয়েমি খৃস্টধর্ম ও তার গির্জার মধ্যে সীমিত রইলো না। বরঞ্চ ধর্ম বলতে যা বুঝায় তা সবই তাদের একগুঁয়েমির শিকার হয়ে পড়লো। ধর্মের বিরুদ্ধে একগুঁয়েমির এরূপ মনস্তাত্ত্বিক অবস্থার সাথে এ দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ যখন জ্ঞানের অঙ্গন থেকে রাজনীতি, অর্থনীতি ও সামাজিক ব্যবস্থার বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রবেশ করলো, তখন গির্জা কর্তৃপক্ষের পরাজয়ের পর নতুন সভ্যতার পতাকাবাহীদের নেতৃত্বে একটি স্থায়ী জীবনদর্শনসহ জীবনের এক নতুন ধর্মীয় প্রাসাদ নির্মাণ করা হলো যার নাম ‘সেকিউলারিজম’। তার মূলনীতি এই যে, রাজনীতি, অর্থনীতি, নৈতিকতা, আইন কানুন, মোটকথা সামাজিক জীবনের কোন বিভাগেই ধর্মের হস্তক্ষেপ করার কোন অধিকার থাকবে না। ধর্ম নিছক এক ব্যক্তিগত ব্যাপার। কেউ তার ব্যক্তিজীবনে খোদা ও পয়গম্বরদেরকে মানতে চায় তো মানতে পারবে। কিন্তু সামাজিক জীবনের সমগ্র বিধি-বিধান প্রণয়নে এ প্রশ্ন অবান্তর যে, এর সম্পর্কে খোদা কি পথনির্দেশনা দান করেন।
আধুনিক জগতের নতুন সভ্যতার চিন্তামূলক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থিনৈতিক ব্যবস্থার প্রাথমিক বুনিয়াদ হলো সেকিউলারিজম (SECULARISM)। ফ্যাসিবাদ, পুঁজিবাদ, নাৎসিবাদ, সমাজবাদ, কমিউনিজম, জাতীয়তাবাদ, সার্বভৌমত্বের দাবিদার গণতন্ত্র, ভোগবাদ (EPICURIANISM), উপযোগবাদ (UTILITARIANISM), নাস্তিকতা, ডারউইনবাদ (DARWINISM) প্রভৃতি মতবাদগুলি সেকিউলারিজমেরই শাখা-প্রশাখা মাত্র এবং সকলের মধ্যে সঞ্চারিত সেকিউলারিজমের প্রাণশক্তি।
এ জীবনব্যবস্থার ভিত্তিপ্রস্তর হচ্ছে ধর্মহীনতা, খোদাদ্রোহীতা অথবা নিছক পার্থিবতা। খোদা ও ধর্মের সম্পর্ক শুধু মানুষের ব্যক্তি জীবনেই সীমিত- এ মতবাদ একটি অর্থহীন ও অবান্তর মতবাদ, জ্ঞান ও বিবেকের সাথে যার কোন দূরতম সম্পর্কও নেই। একথা ঠিক যে, খোদা ও মানুষের ব্যাপার নিম্নের দুইয়ের যে কোন একটি অবশ্যই হবে। হয় খোদা মানুষের এবং এ বিশ্বজগতের স্রষ্টা, প্রভু এবং শাসক ও আইনদাতা, অথবা কোনটাই নন। যদি তিনি স্রষ্টা, প্রভু ও শাসক না হন, তাহলে তার সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক রাখারও কোন প্রয়োজন নেই। আর সম্পর্কহীন কোন সত্তার পূজা-অর্চনা করা একেবারে অর্থহীন। এমনকি এ চিন্তা করাও বিবেকহীনতার পরিচায়ক যে, খোদা তো স্রষ্টা বটে- কিন্তু মানুষ দুনিয়ায় কিভাবে তার জীবন-যাপন করবে, তার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা কেমন হবে তা তিনি বলে দেননি অথবা, মায়াযাল্লাহ, তিনি বলতে অক্ষম। এমন খোদাকে মানার কোন প্রয়োজন আছে কি? কিন্তু তিনি যদি আমাদের এবং বিশ্বজগতের স্রষ্টা, প্রভু ও শাসক হয়ে থাকেন, তাহলে তার শাসন শুধু ব্যক্তিজীবনে সীমিত থাকবে অথবা শাসন নয় নিছক পূজা-অর্চনায় সীমিত থাকবে- এমন চিন্তা করা চরম মূর্খতা বৈ কিছু নয়। এক ব্যক্তির সাথে আর এক ব্যক্তি যুক্ত হওয়ার পর যখন সামাজিক সম্পর্ক শুরু হবে, তখন সেখানে আর স্রষ্টার শাসন-নিয়ন্ত্রণ চলবে না- এ বিবেকহীনের উক্তি হতে পারে। সামাজিক জীবনে মানুষ স্রষ্টার মুখাপেক্ষী না হয়ে যদি স্বাধীন স্বেচ্ছাচারী হয়, তাহলে এ হবে তার স্রষ্টা, প্রভু ও শাসকের বিরুদ্ধে চরম বিদ্রোহ। এ বিদ্রোহের পর যে এ কথা বলে- আমি ব্যক্তিগত জীবনে খোদাকে মেনে চলি- তার মস্তিষ্ক-বিকৃতিই ঘটেছে বলতে হবে। এ স্রষ্টার সাথে ধোঁকা-প্রতারণা ও ভণ্ডামি ছাড়া আর কিছু হতে পারে না।
এটা কি বিবেকহীনের কথা নয় যে, এক এক ব্যক্তি পৃথকভাবে পৃথকভাবে তো খোদার বান্দাহ এবং তাঁর হুকুম মেনে চলতে বাধ্য কিন্তু এ পৃথক পৃথক ব্যক্তিসত্তা মিলিত হয়ে যখন একটা সমাজ গঠন করে তখন আর তারা খোদার বান্দাহ থাকে না। অংশগুলোর মধ্যে প্রত্যেকটি বান্দাহ, কিন্তু অংশগুলোর সমষ্টি বান্দাহ নয়। এ একজন বিবেক-বুদ্ধিহীন পাগলেরই উক্তি হতে পারে। একথা কি করে মেনে নেয়া যায় যে, যদি খোদা এবং তাঁর পথনির্দেশনার প্রয়োজন আমাদের না থাকে আমাদের পারিবারিক জীবনে, আমাদের বস্তি ও শহরে, আমাদের শিক্ষাঙ্গনে, আমাদের হাট বাজারে, আমাদের পার্লামেন্ট ও গভর্নমেন্ট হাউসে, প্রশাসনে, হাইকোর্টে, সেনা ছাউনিতে, পুলিশ লাইনে, যুদ্ধ ও সন্ধিতে, তাহলে তাঁর প্রয়োজন আর কোথায় হবে? যে খোদা এতো অথর্ব ও অযোগ্য (মায়াযাল্লাহ) যে, জীবনের কোন ক্ষেত্রেই তিনি পথ-নির্দেশনা দিতে পারেন না, আমাদের জন্যে কোনটি কল্যাণকর কোনটি অকল্যাণকর তা বলে দিতে পারেন না, আমাদের জীবন সমস্যার সমাধান বলে দিতে পারেন না, তাহলে এমন খোদাকে মেনে লাভ কি? কিন্তু তিনি যদি এসবের প্রকৃত যোগ্য হয়ে থাকেন এবং আমাদের জীবন বিধান দিয়ে থাকেন, তাহলে তা প্রত্যাখ্যান করার অর্থ তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা। এ কারণেই ইংরেজি শব্দ SECULARISM-এর সার্থক বাংলা তর্জমা খোদাদ্রোহিতা ব্যতীত আর কিছু হতে পারে না। বাস্তব জীবনে এ মতবাদটির পরিণাম ফল অত্যন্ত মারাত্মক। জীবনের যে কোন বিভাগ ও দিককে খোদা বা ধর্ম বিবর্জিত করলে তা শয়তানের প্রভাবাধীন হতে বাধ্য। মানুষের প্রাইভেট জীবন বলতে কিছুই নেই। একটি মানবসন্তান মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হবার পর মুহূর্ত থেকেই তার সামাজিক জীবন শুরু হয়। সে তার চারধারে দেখতে পায় তার মা, বাবা, ভাইবোন, দাদা-দাদী, মামু, খালা, ফুফু ও আরও অনেক আত্মীয়-স্বজন। জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হওয়ার পর একটি সমাজ, একটি জ্ঞাতি-গোষ্ঠী, একটা বস্তি, একটি জাতি, একটি সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার সাথে সে সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে। এ ধরনের বহু সম্পর্ক তাকে অন্যান্য মানুষের সাথে এবং অন্যান্য মানুষকে তার সাথে জড়িত করে। এসব সম্পর্ক সঠিক, সুন্দর ও ইনসাফপূর্ণ হলেই এক একটি মানুষের এবং সামগ্রিকভাবে সকল মানুষের কল্যাণ ও সমৃদ্ধি সম্ভব। এ ব্যাপারে একমাত্র আল্লাহতায়ালাই সেই মহাজ্ঞানী সত্তা যিনি মানুষকে এসব সম্পর্ক-সম্বন্ধের জন্য ইনসাফপূর্ন ও স্থায়ী মূলনীতি ও সীমারেখা বলে দিয়েছেন। জীবনের যে কোন বিভাগ ও ক্ষেত্রে আল্লাহতায়ালার হেদায়েত ও পথ-নির্দেশনা প্রত্যাখ্যান করে আপন ইচ্ছামত এবং স্বাধীনভাবে কাজ করতে গেলে কোন স্থায়ী মূলনীতি, ইনসাফ ও সততার কোন স্থান থাকে না। এ জন্যে খোদার হেদায়েত থেকে বঞ্চিত হওয়ার পর প্রবৃত্তি, কুসংস্কার, ত্রুটিযুক্ত অপূর্ণ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ব্যতীত হেদায়েতের জন্যে আর এমনকিছু থাকে না মানুষ যার শরণাপন্ন হতে পারে। এর পরিণাম ফল দেখতে পাওয়া যায় এমন প্রতিটি সমাজে যা ধর্মহীনতা বা নিছক পার্থিবতার (SECULARISM) নীতিতে পরিচালিত হয়। এসব স্থানে দেখা যায় যে, প্রবৃত্তির অভিলাষ চরিতার্থ করার জন্যে প্রতিদিন নিত্য-নতুন মূলনীতি রচিত হয় এবং রহিত করা হয়। মানবীয় সম্পর্ক-সম্বন্ধের এক একটি দিক ও বিভাগ যে কতটা অন্যায়-অবিচার, জুলুম-নিপীড়ন ও পারস্পরিক অনাস্থায় কলুষিত, তা বিশ্ববাসীর কাছে সুস্পষ্ট। সকল মানবীয় ব্যাপারে ব্যক্তিগত, দলীয়, জাতীয় এবং বংশীয় স্বার্থপরতার প্রবল প্রভাব বিদ্যমান। প্রত্যেক জাতি ও দেশ আপন আপন এখতিয়ারের অধীন যথাসাধ্য ও যথাসম্ভব স্বার্থপরতার সাথে আপন আপন অভিলাষ চরিতার্থ করার জন্যে মূলনীতি, আইন-কানুন ও রীতি-পদ্ধতি তৈরি করে নিয়েছে। তারা এ বিষয়ের কোন পরোয়া করে না যে, অন্যান্য ব্যক্তি, দল ও জাতির উপর তার কি প্রতিক্রিয়া হতে পারে। অতএব এ কথা দ্বিধাহীনচিত্তে বলা যেতে পারে যে, সেকিউলারিজম তথা খোদাদ্রোহিতা বা পার্থিবতার পরিণামফল শুধু এই যে, যে ব্যক্তিই এ মতবাদ অনুযায়ী তার কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করবে, সে লাগামহীন, দায়িত্বহীন এবং প্রবৃত্তির দাস হয়ে পড়বে, তা সে কোন ব্যক্তি হোক, দল, দেশ বা জাতি হোক, অথবা জাতিসমষ্টি হোক।
উপরের আলোচনায় এতোটুকু জানা গেল যে, ইহুদী ও খৃস্টধর্মের চরম পতনযুগে ইউরোপে সেকিউলারিজমের জন্ম এবং তা মানবজীবনের সকল স্থান থেকে খোদা ও ধর্মকে উচ্ছেদ করে শুধু ব্যক্তিজীবনের অতি সংকীর্ণ পরিসরে ধর্মকে মেনে চলার অনুমতি দেয়। মোটকথা, সেকিউলারিজম হচ্ছে খোদার সার্বভৌমত্ব এবং পথনির্দেশনা উপেক্ষা করে মানব জীবনের যাবতীয় বিষয়ের ফয়সালা করা এবং আখিরাতের (পরকালীন জীবনের) সাফল্যের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবন এবং তার সাফল্যকে জীবনের লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করা। ‘সেকিউলারিজম’ তার এ অর্থ ও ব্যাখ্যাসহ সমগ্র দুনিয়ার উপর অক্টোপাসের মতো তার বাহু বিস্তার করে আছে। দুনিয়াতে এখনো যদিও খোদা ও ধর্মে বিশ্বাসী লোকদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি, কিন্তু এ ধার্মিকতা সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি জীবনের অতি সংকীর্ণ পরিসরেই সীমিত এবং এ পরিসরের মধ্যেও যারা নিজেদেরকে ধর্মের প্রতি বিশ্বাসী বলে পরিচয় দেন, তাদের অধিকাংশ ধার্মিকতার প্রতি নিষ্ঠাবান নন। বাইরের পরিবেশের প্রভাবে তারা ক্রমশঃ ধর্মের প্রতি, খোদার প্রতি আস্থাহীন হয়ে পড়ছেন। ইউরোপ-আমেরিকায় দেখা যায় গির্জা ও সিনাগগসমূহ পরিত্যক্ত হচ্ছে। ইহুদী-খৃস্টান যুবসমাজ নাস্তিকতার দিকে ঝুঁকে পড়ছে। ব্যক্তিজীবনের অতি সংকীর্ণ পরিসরের বাইরে গোটা জীবনের উপর খোদার পরিবর্তে ‘সেকিউলারিজমের’ প্রভুত্ব-কর্তৃত্ব চলছে এবং বলতে গেলে গোটা মানবজগতের উপর ধর্মের নয়, ‘সেকিউলারিজমের’ রাজত্বই চলছে। এর থেকে অন্য যেসব মতবাদ জন্মগ্রহণ করেছে, যেমন ফ্যাসিবাদ, সমাজবাদ, নাৎসিবাদ, কমিউনিজম, জাতীয়তাবাদ প্রভৃতি যার উল্লেখ পূর্বে করা হয়েছে, এসবের মধ্যে এ বিষয়টি সার্বজনীন মূল্যবোধ হিসেবে বিদ্যমান যে, এসব আল্লাহতায়ালার সন্তুষ্টির উপরে নয়, বরঞ্চ মানবীয় প্রবৃত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত। এ যাবতীয় মতবাদ ও ব্যবস্থাগুলো আল্লাহতায়ালার পথনির্দেশনার ভিত্তিতে গৃহীত নয়, বরঞ্চ খোদাদ্রোহী চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গির ফসল। অতএব দ্বিধাহীনচিত্তে এ কথা বলা যেতে পারে যে, ধর্মহীনতা ও খোদাদ্রোহীতার অপর নামই ‘সেকিউলারিজম’।
‘সেকিউলারিজমকে’ ইসলামের মুকাবিলায় জাহেলিয়াতের মারাত্মক অস্ত্র এজন্যে বলা হয়েছে যে, তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস পোষণকারী মুসলমান জাতিও দ্বিধাহীনচিত্তে ‘সেকিউলারজমকে’ তাদের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে নীতি নির্ধারক মতবাদ হিসেবে গ্রহণ করেছে। এ মতবাদের উৎপত্তি হয়েছিল খৃস্টান ধর্মীয় পণ্ডিতদের ধর্মের নামে মনগড়া শাসন ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আধুনিক চিন্তাশীল ও বিজ্ঞানীদের বিদ্রোহী ঘোষণার মাধ্যমে। তাওরাত ও ইঞ্জিল (বাইবেল) এতোটা বিকৃত ও পরিবর্তিত যে, তার মধ্যে খোদার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ মূল বাণীর অতি সামান্য অংশই খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। তাছাড়া বাইবেলে রাজনীতি, অর্থনীতি, বিচার বিভাগ, যুদ্ধ-সন্ধি প্রভৃতি বিষয়ে কোন নীতিমালা ঘোষণা করা হয়নি। যার ফলে দেশ পরিচালনায় এবং যাবতীয় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে কোন ভারসাম্যপূর্ণ ও সুবিচারপূর্ণ নীতি অবলম্বন করা সম্ভব ছিল না। ধর্মীয় পণ্ডিত তথা পাদ্রীগণ তাদের নিজেদের স্বার্থে ধর্মের নামে এক ধর্মহীন ও শোষণমূলক শাসন কায়েম রেখেছিলেন যার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ ‘সেকিউলারিজম’ জন্মলাভ করেছে। কিন্তু মুসলমানদের ব্যাপার সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাদের সামনে কুরআন ও সুন্নাহ ছিল এবং এখনো আছে। প্রায় অর্ধ শতাব্দীব্যাপী অবিকৃতভাবে বিদ্যমান এক নজিরবিহীন ইসলামী কল্যাণরাষ্ট্রের দৃষ্টান্তও তাদের সামনে রয়েছে। এতদসত্ত্বেও আল্লাহর সার্বভৌমত্ব অর্থাৎ জীবনের সকল ক্ষেত্রে তাঁর প্রভুত্ব ও কর্তৃত্ব প্রত্যাখ্যান করে মানুষের রচিত মতবাদ ও আইনের কাছে তাদের মাথানত করা জাহেলিয়াতের এক বিরাট কৃতিত্বই বলতে হবে।
তবে একথা ঠিক যে, মুসলমানগণ তাদের নৈতিক অধঃপতনের কারণে রাজনৈতিক ক্ষমতা থেকে অপসারিত হওয়ার পর যখন গোলামির জীবন যাপন করে, তখন বিজয়ী শক্তির চিন্তাধারা, জীবনদর্শন, জীবনের মূল্যবোধ তাদরকে প্রভাবিত করে। অবশেষে তারা বিজয়ী শক্তির এমন মানসিক দাসে পরিণত হয় যে, তারা সবকিছু তাদের মন দিয়ে চিন্তা করতে থাকে এবং তাদের চোখ দিয়েই দেখতে থাকে।
ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শাসনের অধীনে সেকিউলারিজম
এ উপমহাদেশের পূর্বাঞ্চলে অর্থাৎ বাংলা-বিহার-উড়িষ্যায় ইংরেজ জাতির ঔপনিবেশিক শাসনের সূত্রপাত হয় ১৭৫৭ খৃস্টাব্দে। শঠতা, প্রতারণা, উৎকোচ ও বিশ্বাসঘাতকতার মাধ্যমে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার স্বাধীন শাসনকর্তা সিরাজউদ্দৌলাকে বিনাযুদ্ধেই পরাজিত ও নিহত করে এ অঞ্চলে এবং পরবর্তী একশ’ বছরের মধ্যে সমগ্র উপমহাদেশে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। ইংরেজ শাসনের পূর্বে গোটা উপমহাদেশে কয়েকশ’ বছর যাবত মুসলিম শাসন বলবৎ ছিল। উল্লেখ্য যে, মুসলিম শাসন আমলে দেশের সর্বত্র ইসলামী আইন প্রবর্তিত ছিল এবং সকল জাতি ও ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে পরিপূর্ণ সুবিচার প্রতিষ্ঠিত ছিল। মুসলমানদেরকে ক্ষমতাচ্যুত করার পর ইংরেজ শাসক হয়ে বসে এবং তারপর দেশের প্রচলিত ইসলামী আইন রহিত করে তদস্থলে মানব রচিত আইন কার্যকর করা হয়।
মুসলিম শাসকদের চরম নৈতিক অধঃপতন, ভোগ বিলাস ও দায়িত্বহীনতার কারণেই মুসলিম শাসনের অবসান হয়েছিল। কিন্তু মুসলমানগণ দু’টি কারণে বিদেশী ও বিধর্মীদের শাসন মেনে নিতে পারেনি। এক- শাসকের জাতি হয়ে তাদেরকে পরাধীনতা তথা গোলামির শৃঙ্খল পরতে হয়েছিল যা তাদের জন্যে ছিল একেবারে লজ্জাকর ও অসহনীয়। দুই- ইসলামী আইনের পরিবর্তে মানবরচিত খোদাহীন তথা সেকিউলার আইন তাদের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল। তা ছিল তাদের ঈমান-আকীদার পরিপন্থী।
ইসলামের মৌল বিশ্বাস অনুযায়ী আল্লাহতায়ালা শুধু মানবজাতিসহ বিশ্বজাহানের স্রষ্টাই নন, বরঞ্চ তিনি সকল জীবের রিযিকদাতা, প্রতিপালক, প্রভু, বাদশাহ ও আইনদাতা। কুরআনের সূরা ‘আন নাসে’ আল্লাহতায়ালাকে মানবজাতির বাদশাহ বলে অভিহিত করে তাঁর কাছে আশ্রয় চাইতে বলা হয়েছে। আল্লাহ মানবজাতির বাদশাহ এবং মানুষ তাঁর প্রজা। বাদশাহের পক্ষ থেকে প্রজার জন্যে অবশ্যই প্রয়োজনীয় আইন-কানুন নির্ধারিত থাকবে যা প্রজার জন্যে অবশ্য পালনীয়। অন্যথায় আইন লংঘনের অপরাধে শাস্তির যোগ্য অবশ্যই হতে হবে।
এই উপমহাদেশের মুসলমানদের নিকটে এ প্রশ্নটি প্রকট হয়ে দেখা দেয় যে, আল্লাহর আইনের পরিবর্তে মানুষের রচিত আইন কি করে মেনে নেয়া যায়। আল্লাহর আইন-শাসন রহিত করে যে বা যারা নিজেদের আইন-শাসন মানবসমাজে কার্যকর করতে চায়, তারা খোদায়ীর দাবিদার বাতিল শক্তি যাদেরকে কুরআনের ভাষায় ‘তাগুত’ বলা হয়েছে। আর তাগুতের হুকুম-শাসন, প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব প্রত্যাখ্যান করেই আল্লাহর উপর ঈমান আনতে হবে। একই সাথে আল্লাহ ও তাগুতের আনুগত্য অযৌক্তিক ও ইসলামের মৌল বিশ্বাসের পরিপন্থী। অবশ্যি এ কথা ঠিক যে, ব্রিটিশ সরকার এ উপমহাদেশে তাদের প্রায় দু’শ’ বছর শাসনকালে মুসলমানদের নামায, রোযা, হাজ্জ্ব, যাকাত প্রভৃতি ধর্ম-কর্মে কোন বাধা দান করেনি। তাদের কথা ছিল, প্রত্যেকেই তার নিজ নিজ ধর্মকর্ম করার পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করবে। কিন্তু দেশের আইন-কানুন, বিচার ব্যবস্থা, রাজনীতি, অর্থনীতি, সভ্যতা-সংস্কৃতি, শিক্ষা-দীক্ষা প্রভৃতির উপর ধর্মের কোন অনুশাসন থাকবে না। আধুনিক পরিভাষায় যাকে বলা হয় ‘সেকিউলারিজম’। এতে ব্যক্তি জীবনের বাইরে জীবনের সকল ক্ষেত্রে খোদার আইন-কানুন ও প্রভুত্ব-কর্তৃত্ব পুরোপুরি অস্বীকার করা হচ্ছে। চরম খোদাদ্রোহীতা ছাড়া একে আর কি বলা যেতে পারে?
ইসলামের পরিপন্থী এ দর্শন এবং সমাজব্যবস্থা মুসলমানগণ মেনে নিতে পারেননি যার জন্যে সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ বেরেলভী (র) ‘তাহরিকে মুজাহেদীন’ নামে সত্যিকার অর্থে এক ইসলামী আন্দোলন শুরু করেন। উপমহাদেশের সকল অঞ্চল থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এ আন্দোলনে হাজার হাজার মুসলমান যোগদান করেন। অতঃপর তাঁরা আল্লাহর পথে সশস্ত্র যুদ্ধ পরিচালনা করে একটি নির্ভেজাল ইসলামী রাষ্ট্রও কায়েম করেন। তা যদিও স্থায়ী হতে পারেনি নানান কারণে তথাপি আল্লাহতায়ালার প্রকৃত বান্দাহগণ তাগুতী আইনের শাসন উৎখাত করে অল্পকালের জন্যে হলেও আল্লাহর আইন-শাসন কায়েম করে তাঁদের ঈমানী দায়িত্ব পালন করেছেন।
জাহেলিয়াত তথা শয়তানের এ এক বিরাট কৃতিত্বই বলতে হবে যে, সে সামগ্রিকভাবে মুসলিম জাতিকে এ খোদাদ্রোহী দর্শনের (সেকিউলারিজম) প্রতি প্রভাবিত ও উদ্বুদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছে। যারা খোদার অস্তিত্বে বিশ্বাসী নয়, অথবা যারা তিন খোদা কিংবা বহু খোদার অস্তিত্বে বিশ্বাসী তাদের এ দর্শন মেনে নিতে কোন অসুবিধা নেই। ইসলাম ব্যতীত অন্য ধর্মে যারা বিশ্বাসী, তাদের ধর্মের পক্ষ থেকে কোন জীবনবিধান ঘোষণা করা হয়নি। কিছু পূজা-অর্চনা ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন ব্যতীত জীবনের বিভিন্ন দিক ও বিভাগ সম্পর্কে কোন পথনির্দেশনা দেয়া হয়নি। এমনকি আসমানী গ্রন্থ ইঞ্জিলেও সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি। আল্লাহপাকের সর্বশেষ ঐশীগ্রন্থ ‘আল কুরআন’-এ মানুষের সমগ্র জীবনের জন্যে পরিপূর্ণ বিধান দেয়া হয়েছে। জীবনের যে কোন ক্ষেত্রে কোন বিষয়ের বিচার-ফয়সালা করতে হলে তা আল্লাহর নাযিল করা আইন-বিধান অনুযায়ী করতে হবে। তা যারা করেন না তাদেরকে সুস্পষ্ট ভাষায় ‘কাফের’ ‘জালেম’ ও ‘ফাসেক’ বলা হয়েছে। কিন্তু মুসলমান নামে পরিচিত ব্যক্তি ও ব্যক্তিবর্গ দ্বিধাহীনচিত্তে এ সুস্পষ্ট নির্দেশ লঙ্ঘন করে চলেছে। এর একমাত্র কারণ এ ছাড়া আর কী হতে পারে যে, এসব হতভাগ্য মুসলমান ইসলাম-বিরোধী শক্তির অধীনে রাজনৈতিক গোলামির জীবন যাপন করে এবং তাদের প্রবর্তিত শিক্ষা মেনে নিয়েছে। এ তাদের চরম হীনমন্যতা ও মানসিক গোলামি ছাড়া আর কিছু নয়।
পরম পরিতাপের বিষয়, মুসলিম জগতের দেশগুলোর মধ্যে সর্বপ্রথম তুরস্ক সমাজ, রাষ্ট্র এবং সভ্যতা-সংস্কৃতির পুনর্গঠনে সেকিউলারিজমকে বুনিয়াদ হিসেবে গ্রহণ করে। এ খোদাদ্রোহী রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থার স্থপতি ছিলেন মুস্তাফা কামাল পাশা।
কামাল পাশা ১৮৮১ খৃস্টাব্দে সালোনিকার এক জীর্ণ কুটিরে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা আলী রেজা সরকারি অফিসে কেরানীগিরি করতেন। দারিদ্র্যের নিপীড়ন সহ্য করতে না পেরে চাকুরি ছেড়ে ব্যবসা শুরু করেন ভাগ্য পরিবর্তনের আশায়। কিন্তু ব্যবসায় তিনি কোন উন্নতি করতে পারেননি। বরঞ্চ ক্রমশঃ অধিকতর দারিদ্র্যের সম্মুখীন হন। অবশেষে জীবন সম্পর্কে চরম হতাশা তাকে মাদকাসক্ত করে ফেলে এবং তিনি যক্ষ্মারোগে প্রাণত্যাগ করেন। তার স্ত্রী অর্থাৎ মুস্তাফা কামালের মা ছিলেন অত্যন্ত খোদাভীরু মুসলমান এবং পর্দানশীন। তিনি চেয়েছিলেন তার ছেলেকে একজন ধার্মিক পণ্ডিত বানাতে। কিন্তু শৈশবকাল থেকে কামাল ছিলেন দুর্বিনীত ও উচ্ছৃংখল চরিত্রের। শিক্ষকদের প্রকাশ্যে অপমানিত ও গালাগালি করা তার স্বভাব ছিল। ফলে স্কুলে লেখাপড়া তার হয়নি। পরে তার চাচা তাকে সামরিক স্কুলে ভর্তি করে দেন। এভাবে সামরিক বাহিনীতে যোগদানের তার সুযোগ হয়।
কামাল পাশা ছোটোবেলা থেকেই ইসলাম ও ইসলামী আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি একেবারে বীতশ্রদ্ধ ছিলেন। এসব ব্যাপারে তিনি তার মায়ের উপদেশ-নসিহত শুধু প্রত্যাখ্যানই করতেন না, তার সাথে খুব রূঢ় আচরণও করতেন। খোদা, ওহী, নবুওত, আখিরাত প্রভৃতির প্রতিও তার অবিশ্বাস দানা বাঁধতে থাকে এবং তিনি পরিণত বয়সে একজন নাস্তিক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন।
প্রথম মহাযুদ্ধ
বিগত প্রথম মহাযুদ্ধে ‘ইউরোপের রুগ্ন ব্যক্তি’ (The Sick Man of Europe) তুরস্ক ইংরেজদের বিরুদ্ধে জার্মানীর পক্ষে যুদ্ধ করে। সে সময় পর্যন্ত তুরস্কের ওসমানীয়া সাম্রাজ্য খিলাফতের রক্ষণাবেক্ষণকারী হিসেবে গণ্য হতো। প্রতিপক্ষকে চরম আঘাত এবং মুসলিম ঐক্য ভেংগে চুরমার করার উদ্দেশ্যে ‘লরেন্স অব অ্যারাবিয়া’কে ইংরেজগণ আরব জাতীয়তাবাদের প্রচারক হিসেবে আরব দেশে প্রেরণ করে। মক্কার তৎকালীন শাসক শরীফ হুসাইন হাশমী এ জাতীয়তাবাদের প্রচারণায় এতোটা প্রভাবিত হয়ে পড়েন যে, ১৯১৫ সালের মাঝামাঝি আরবদের জাতীয় স্বাধীনতার জন্য মুসলমানদের বিরুদ্ধেই অস্ত্রধারণ করে তুরস্কের পৃষ্ঠে ছুরিকাঘাত করেন। প্রথম মহাযুদ্ধে ইংরেজ তথা সম্মিলিত বাহিনী (Allied Force) বিজয় লাভ করে। তারা যুদ্ধের প্রারম্ভেই এক গোপন চুক্তির মাধ্যমে ওসমানীয়া সাম্রাজ্যকে তাদের নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে রেখেছিল। ১৯১৯ সালে যুদ্ধ শেষে তুরস্ক সাম্রাজ্যকে ছিন্নভিন্ন করে দেয়া হয়। ইউরোপীয় অংশ তার হাতছাড়া হয়। আরব জাতীয়তাবাদের বিষক্রিয়ার ফলে আরব দেশগুলো তুরস্ক সাম্রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লো বটে কিন্তু সেগুলোকে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও গ্রীসের মধ্যে বণ্টন করে দেয়া হলো। অবশেষে ওসমানীয়া সাম্রাজ্য প্রাচীন আনাতোলিয়াতে (ইস্তাম্বুল) সীমিত হয়ে রইলো। ১৯১৯ সালের মে মাসে ওসমানিয়া রাজধানীতে শুধুমাত্র নামসর্বস্ব সুলতানের অস্তিত্ব রয়ে গেল। কিন্তু এখানেও তার স্বাধীনতা ছিল বিপন্ন।
এদিকে ব্রিটিশ ভারতের তথা এ উপমহাদেশের মুসলিম নেতৃবৃন্দ মুসলমানদের মনে এ বিশ্বাস সৃষ্টি করেছিলেন যে, খলিফাতুল মুসলিমীন এবং খিলাফত ব্যবস্থা তাদের প্রকৃত ঈমানের অংগ-অংশ। অতঃপর ওসমানীয়া সাম্রাজ্যের পতন ও তার ছিন্নভিন্ন অবস্থাদৃষ্টে উপমহাদেশের মুসলমানদের মনে এ সন্দেহের উদ্রেক হয় যে, ব্রিটিশ হয়তো খিলাফতের কেন্দ্রকেই ধ্বংস করে দেবে যাকে মুসলমানগণ তাদের দ্বীনী এবং রূহানী কেন্দ্র মনে করতো।
অতঃপর মুসলিম নেতৃবৃন্দ ভারতের বড়লাটের সাথে দেখা করে তাদের মনোভাব ব্যক্ত করেন। তাদের সাক্ষাৎ সন্তোষজনক হয়নি। অতঃপর মাওলানা মুহাম্মাদ আলী জওহর, মাওলানা সাইয়্যেদ সুলায়মান নদভী প্রমুখ নেতৃবৃন্দের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল লন্ডনে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের সাথে সাক্ষাৎ করে তাদের বক্তব্য পেশ করেন। প্রত্যুত্তরে তাদেরকে বলা হয় যে, মূল তুরস্কের ভূখণ্ড ব্যতীত অন্যান্য এলাকাসমূহ তাদেরকে দেয়া যাবে না।
ব্রিটিশ সরকারের এ ধরনের মুসলিম-বিদ্বেষী আচরণে উপমহাদেশের মুসলমানগণ অতিশয় ক্ষুব্ধ হয়ে পড়েন এবং খিলাফতের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্যে ভারতে প্রচণ্ড খিলাফত আন্দোলন শুরু হয়। এ বছরের (১৯১৯) ১০ আগস্ট সমগ্র উপমহাদেশে খিলাফত দিবস পালন করা হয়। এবং এ সময় থেকে বিভিন্ন স্থানে হরতাল পালিত হতে থাকে। মোটকথা, উপমহাদেশে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ শুরু হয়। এক মাসের মধ্যে প্রায় বিশ হাজার মুসলমান স্বেচ্ছায় কারাবরণের জন্যে নিজেদেরকে পেশ করেন। এ আন্দোলন ১৯২২ সাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। কিন্তু পরম পরিতাপের বিষয়, এতো বড়ো আন্দোলন ও ব্রিটিশ বিরোধী বিক্ষোভ বিস্ফোরণ সবই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।
তার কারণ এই যে, কামাল পাশা তুরস্কের মুসলমানদের জিহাদী প্রেরণার সুযোগ গ্রহণ করে অসাধারণ বীরত্ব ও বিচক্ষণতার সাথে যুদ্ধ পরিচালনা করেন এবং বহু এলাকা ইংরেজদের নিকট থেকে পুনরুদ্ধার করেন। তুরস্কবাসীদের একতাবদ্ধ করেন এবং তাদের হৃত মর্যাদা ও গৌরব পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হন। এভাবে একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার পর কামাল পাশা ১৯২২ সালের নভেম্বর মাসে ওসমানীয়া খিলাফতের সুলতান মুহাম্মাদ হাশিমকে ক্ষমতাচ্যুত করেন এবং ১৯২৪ সালের মার্চ মাসে কাষ্ঠপুত্তলিসম সর্বশেষ সুলতান আব্দুল মজিদকে দেশ থেকে বহিষ্কার করে খিলাফতের উচ্ছেদ সাধন করেন।
ক্ষমতাগ্রহণের পর পরই কামাল পাশা ঘোষণা করেন যে, তিনি তুর্কী জাতির জীবন থেকে ইসলামের সকল চিহ্ন মুছে ফেলবেন। শুধুমাত্র ইসলামের কর্তৃত্ব নির্মূল করার পরই তুর্কীরা অগ্রগতি লাভ করতে পারে এবং সম্মানিত আধুনিক জাতিতে পরিণত হতে পারে। তিনি এভাবে ইসলাম ও ইসলামের সকল দিকের বিরুদ্ধে জনসমক্ষে একের পর এক ভাষণ দিতে থাকেন।
তিনি ১৯২৪ সালের তেসরা মার্চ সম্পূর্ণ ‘সেকিউলার’ তুর্কীজাতি প্রতিষ্ঠার জন্য পরিষদে বিল উত্থাপন করেন। তিনি বলেন, ধর্ম ও রাষ্ট্রকে পৃথক করতে হবে। তুর্কী প্রজাতন্ত্রকে সত্যিকার অর্থে সেকিউলার রাষ্ট্রে পরিণত করতে হবে।
বিলের বিরোধিতাকে তিনি মারাত্মক অপরাধ হিসেবে ঘোষণা করেন এবং তার ভয়াবহ পরিণতির জন্য সকলকে সাবধান করে দেন। পরবর্তী পর্যায়ে কোন বিতর্ক ছাড়াই বিলটি গৃহীত হয়।
এখানে সেকিউলার শব্দের অন্তর্নিহিত অর্থ যে ধর্মহীনতা বা খোদাদ্রোহীতা তা রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপে প্রমাণিত। খোদাহীন জড়বাদী পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণে পানাহার, পোশাক পরিচ্ছদ, চালচলন, অশ্লীল নাচগান, মদ্যপান ও অন্যান্য ইসলাম-বিরোধী সংস্কৃতি তুরস্কের জাতীয় প্রতীক বলে ঘোষণা করা হয়। ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে ইসলামী শিক্ষা উচ্ছেদ করা হয়। ফলে বহু মাদ্রাসা-মক্তব ধ্বংস হয়ে যায়। তুরস্কের নিজস্ব ভাষার প্রাচীন বর্ণমালা পরিবর্তন করে রোমান বর্ণমালা প্রবর্তন করা হয়। আরবিতে আজান নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। আকস্মিকভাবে শুধু ক্ষমতার দাপটে একটি মুসলিম জাতিকে ইসলামবিমুখ জাতিতে পরিণত করা হয়।
কিছুকাল পর তুরস্কের একটি প্রতিনিধিদল দিল্লী আগমন করেন। তারা নিজেদেরকে বার বার ইউরোপীয় জাতি হিসেবে পরিচয় দিতে গর্ববোধ করেন। দিল্লীর মুসলমানগণ তাদেরকে দিল্লী জামে মসজিদে জুমার নামায আদায়ের আমন্ত্রণ জানান। কিন্তু সে আমন্ত্রণ তারা প্রত্যাখ্যান করেন। আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণও তারা প্রত্যাখ্যান করেন। অথচ পূর্ব থেকে কোন কর্মসূচি না থাকলেও বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় তারা আনন্দের সাথে পরিদর্শন করেন। অর্থাৎ মুসলমান বলে পরিচয় দিতে তারা রাজি ছিলেন না। এ হলো সেকিউলারিজমের বাস্তব পরিণাম ফল।
সেকিউলারিজমের পতাকাবাহীগণ বলেন, সেলিউলারিজম ধর্মবিরোধী নয়। তবে ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে পৃথক মনে করে। এ একটা মনভোলানো প্রতারণা মাত্র। তুরস্কের সেকিউলারিজমের স্থপতি ধর্মের প্রতি কোন বিশ্বাস রাখতেন না এবং ইসলাম নির্মূল করাই তার বাসনা ছিল। তিনি বলতেন, ইসলাম একজন ধর্মতাত্ত্বিক নীতিহীন আরবের প্রচলিত একটি মৃত বস্তু। এখানে নবী মুহাম্মাদের (সা) প্রতিই তিনি ইংগিত করেছেন, তাতে সন্দেহ নেই।
তিনি আরও বলেন, সম্ভবতঃ এটি মরুর উপজাতিদের জন্যে উপযোগী ছিল। বর্তমান আধুনিক ও প্রগতিশীল রাষ্ট্রের জন্যে এর তেমন মূল্য নেই। খোদার ওহী? কোন খোদাই তো নেই! এগুলো হচ্ছে শৃঙ্খল, যার দ্বারা মোল্লা এবং অসৎ শাসকগণ জনগণকে নতশির হয়ে থাকতে বাধ্য করে।
খোদা ও ধর্মের প্রতি যার অবিশ্বাস, তার চরিত্রও সে ধরনের হয়ে থাকে। সে হয় চরম স্বেচ্ছাচারী, নিষ্ঠুর চরিত্রহীন ও আত্মগর্বিত। কামাল পাশাও ছিলেন সেই চরিত্রের। তিনি লতিফা নাম্নী একজন শিক্ষিতা সুন্দরী মহিলাকে বিয়ে করেন। তিনি এ মহিলাকে পুরুষের পোশাক পরিধান এবং মহিলাদের নিরংকুশ সাম্যের দাবি করতে উৎসাহিত করেন। কিন্তু আত্মসম্মানবোধসম্পন্না হয়ে যখন তিনি সম্মানিত স্ত্রীর মতো আচরণ দাবি করেন, তখন রাগান্বিত হয়ে কামাল তাকে তালাক দেন। তালাক দেওয়ার পর তার লজ্জাহীনতা সীমালঙ্ঘন করে। তিনি এতো বেশি মদ্যপান শুরু করেন যে, একেবারে দুর্দান্ত মদখোর বনে যান এবং প্রায় মদালস হয়ে পড়তেন। সুন্দর যুবক ছেলেরাই তার কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থের লক্ষ্য হয়ে পড়ে। তার রাজনৈতিক সমর্থকদের স্ত্রী-কন্যাদের প্রতি তার আচরণ এতোই অশালীন হয়ে পড়ে যে, তারা তাদের মহিলাদেরকে তার কাছ থেকে যথাসম্ভব দূরে রাখার চেষ্টা করতেন। যৌনব্যাধিতে তার স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ে।
তিনি কাউকে বিশ্বাস করতেন না। তার নিজের মতের কোন বিরোধী মতের প্রতি তিনি কর্ণপাত করতেন না। তিনি সব কাজ আত্মস্বার্থের মাপকাঠিতে বিবেচনা করতেন।
কোন স্বৈরাচারী শাসক তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে কিছুতেই বরদাশত করতে পারে না। কামাল পাশাও তার রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীকে নির্মূল করার কোন সুযোগই হাতছাড়া করেননি। তাদের বিচারের জন্যে একটি স্বৈরাচারী ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়। কোন বিচার-পদ্ধতি বা সাক্ষ্য-প্রমাণ ছাড়াই তাদের মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়।
কামালের ইসলাম বিরোধী সংস্কার অভিযান তুর্কী জনগণ মেনে নিতে পারেনি। তাদের বিক্ষোভ দানা বাঁধতে থাকে। ১৯২৬ সালে পার্বত্য অঞ্চলের কুর্দী উপজাতিরা কামাল প্রশাসনের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। কামাল পাশা তুর্কী কুর্দিস্থানে বর্বর অত্যাচার শুরু করেন। গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দেন। গৃহপালিত পশু ও শস্যক্ষেত ধ্বংস করেন। মহিলা ও শিশুদের পাইকারীভাবে ধর্ষণ ও হত্যা করা হয়। বহু কুর্দী নেতাকে জনসমক্ষে ফাঁসি দেয়া হয়। আর্তনাদ, হাহাকার ও মার্সিয়া মাতমের ভেতর দিয়ে কামাল তার স্বৈরাচারী ও ইসলাম-বিরোধী সেকিউলার শাসন পাকাপোক্ত করেন।
কিন্তু তুরস্ক থেকে ইসলাম নির্মূল করা যায়নি। কামালবাদের পতন শুরু হয়েছে এবং শুরু হয়েছে ইসলামের নবজাগরণ। যুব সমাজে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে, সেনাছাউনিতে। জাহেলিয়াতের অস্ত্র কামালবাদ এখন ক্ষয়িষ্ণু। ইসলামের নবজাগরণকে ঠেকাবার শক্তি তার আর নেই।
‘সেকিউলারিজম’-এর ভিত্তিতে যে জীবনদর্শন রচিত হয়েছিল, ন্যায়-অন্যায়, ভালোমন্দ, লাভ-লোকসান, জয়-পরাজয় ও পাপপুণ্যের যে মানদণ্ড নির্ধারিত হয়েছিল এবং যে সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রাসাদ গড়ে উঠেছিল, তার প্রভাব প্রতিপত্তি ক্রমশঃ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতি অগ্রগতির মাধ্যমে এ নতুন সভ্যতা মানুষের মনে এক চমক ও আকর্ষণ সৃষ্টি করে। ফ্রান্সিস বেকন, ভলটেয়ার, ডারউইন, হেগেল, কার্ল মার্কস, ফ্রয়েড প্রমুখ চিন্তাশীল পণ্ডিতদের নতুন নতুন চিন্তাধারা এ সভ্যতা-সংস্কৃতিকে নাস্তিক্য ও জড়বাদিতার পাতাকাবাহী বানিয়ে দেয়। মুসলিম দেশগুলো এক একটি করে এ সভ্যতা-সংস্কৃতি ও তার রাজনৈতিক আধিপত্যের কাছে মাথা নত করে। গোলামির জীবন যাপন তাদের মধ্যে মানসিক পরিবর্তন এনে দেয়। ইসলামী আকীদাহ-বিশ্বাস, চারিত্রিক মান এবং তাওহীদের প্রতি বিশ্বাসজনিত অদম্য সাহস, বিরাট মনোবল ও শৌর্যবীর্য তারা হারিয়ে ফেলে। বিজয়ী সভ্যতার অধীন সেকিউলার তথা খোদাহীন শিক্ষাব্যবস্থা তাদেরকে একেবারে খোদাবিমুখ বানিয়ে দেয়। নামে তারা মুসলমান রইলো বটে, কিন্তু আখিরাতে খোদার কাছে জবাবদিহির কোন অনুভূতিই তাদের মনের মধ্যে বিদ্যমান রইলো না।
কিন্তু গোটা মুসলিম সমাজের অবস্থা একই রকম ছিল না। জনসাধারণের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ লোক এমন ছিল যাদের কিছুটা বিকৃতি ঘটে থাকলেও তাদের মধ্যে ইসলামী চেতনা ও প্রাণশক্তি বিদ্যমান ছিল। কিন্তু তারা ঐক্যবদ্ধ ছিল না এবং সঠিক পথে নের্তৃত্ব দেয়ার লোকেরও বড়ো অভাব ছিল। আলেম সমাজ ইসলামকে জিইয়ে রাখার জন্যে এতোটুকু করেছেন যে, ইসলামী শিক্ষার জন্যে নিজেদের উদ্যোগে মাদ্রাসা-মক্তব, দারুল উলুম কায়েম রেখেছেন, কুরআন-হাদীসের ইলম চর্চা বজায় রেখেছেন। বিভিন্ন স্থানে ইলমে তাসাউফ শিক্ষা দানের খানকাও গড়ে উঠেছে। কিন্তু এসবের দ্বারা তারা জাহেলিয়াতের অগ্রগতিকে রুখতে পারেননি। জাহেলিয়াত মানবজীবনের সর্বত্র- শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে সরকারি প্রশাসন ও বিচারালয় পর্যন্ত; বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম থেকে আন্তর্জাতিক যোগাযোগ ও সম্পর্ক-সম্বন্ধ পর্যন্ত, আহার-বিহার, খেলাধুলা, আমোদ-প্রমোদ ও আপ্যায়নে, বিয়ে-শাদী, বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও পর্বাদিতে- তার সর্বময় কর্তৃত্ব-প্রভুত্ব কায়েম করেছে। তাগুতী সরকারগুলো তাদের প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে এমন কিছু লোক তৈরি করতে থাকে যারা প্রশাসনকার্যে তাদের সাহায্য করবে এবং সময় এলে তাদের ওপরই দেশের শাসনভার অর্পিত হবে। ইসলামী জ্ঞান ও চরিত্র বিবর্জিত এসব লোক তাদের পশ্চিমী প্রভুদের মনোরঞ্জনের জন্যে তাদের অন্ধ অনুকরণ করতে থাকে। তারা মন থেকেই ইসলামকে বিদায় দিয়েছিল। কারণ তাদের বিশ্বাস, মুসলমান জাতির উন্নতি-অগ্রগতির পথে ইসলাম বিরাট প্রতিবন্ধক।
পাশ্চাত্য সভ্যতা সংস্কৃতির মানসপুত্র এসব বিকৃত ও বিপথগামীদের ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে এক সময়ে সুসংবাদ শোনানো হল। লর্ড ক্রোমার তার রচিত ‘হিস্ট্রী অব মডার্ন ইজিপ্ট’ গ্রন্থে ব্রিটিশ সরকারের মুখপাত্র হিসেবে বলেন-
England is prepared to grant eventual political freedom to all of her colonial possessions as soon as a generation of intellectuals and politicians imbued through English education with our ideals & culture, is ready to take over. But we shall not tolerate for a single moment the establishment of an independent Islamic state anywhere in the world.
অর্থাৎ ইংল্যান্ড তার ঔপনিবেশিক শাসনাধীন দেশগুলোকে চূড়ান্তভাবে রাজনৈতিক স্বাধীনতা দানে প্রস্তুত যখনই রাজনীতিবিদ ও বুদ্ধিজীবীদের একটি প্রজন্ম ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে আমাদের আদর্শ ও সংস্কৃতির প্রতি উদ্বুদ্ধ হয়ে ক্ষমতা গ্রহণের জন্যে তৈরি হবে। কিন্তু দুনিয়ার কোথাও কোন স্বাধীন ইসলামী রাষ্ট্র আমরা এক মুহূর্তের জন্যেও বরদাশত করব না।
লর্ড ক্রোমার শুধু ব্রিটিশ শাসকদের মনের কথাই বলেননি, ইউরোপের সকল সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মনের কথা ছিল তাই। আমরা দেখতে পাই যে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর মুসলমান দেশগুলোতে যখন স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু হয়, তখন মুসলমান জনসাধারণ ইসলামী জিহাদী প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু সর্বত্র একই দৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। স্বাধীনতা লাভের পর একটি বিশেষ চক্র (পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্ধ অনুসারী) ক্ষমতা হস্তগত করে এবং মুসলমানদের আশা-আকাংক্ষা নির্মূল করে ইসলামী শাসনের পরিবর্তে তাগুতী শাসনই কায়েম করে। এভাবে জাহেলিয়াত বিজয় লাভ করে। নতুন স্বাধীনতা লাভকারী প্রায় প্রতিটি মুসলিম দেশে একই অবস্থা দেখতে পাওয়া যায়।
প্রথম মহাযুদ্ধের পরই এ উপমহাদেশে স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু হয়। তিরিশের দশকে এ আন্দোলন জোরদার হয়। হিন্দু ও মুসলমান পৃথক দু’টি জাতি এ উপমহাদেশে কয়েক শতাব্দী যাবত পাশাপাশি বসবাস করে আসলেও তাদের নিজ নিজ জাতীয় স্বাতন্ত্র্য-স্বকীয়তা তারা অক্ষুণ্ণ রেখেছে। হিন্দু এখানকার সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতি। তারা ভৌগোলিক জাতীয়তার দাবি উত্থাপন করে বলে- এ দেশে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলে মিলে এক জাতি, ‘মুসলমান’ বলে পৃথক কোন জাতির অস্তিত্ব এখানে নেই। এ দাবি ছিল হাস্যকর, অবাস্তব ও সত্যের পরিপন্থী।
উপমহাদেশের দশ কোটি মুসলমানের পক্ষ থেকে হিন্দুদের দাবি প্রত্যাখ্যান করে জানানো হলো- মুসলমানগণ তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের ভিত্তিতে একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জাতি। মুসলমান এবং অমুসলমান মিলে কোন একদিন এক জাতি ছিলও না এবং তা হতেও পারে না।
হিন্দুদের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের দাবি ছিল এক জাতীয়তার ভিত্তিতে এখানে একটি সেকিউলার রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা।
মুসলমানদের দাবি ছিল- যেহেতু মুসলমান একটি আলাদা জাতি এবং তাদের ঈমান-আকীদার দাবি অনুযায়ী ইসলামের তথা কুরআনেরই পূর্ণাংগ শাসন কায়েম করতে হবে, অতএব এ ইসলামী শাসনের জন্যে মুসলমানদের একটি স্বতন্ত্র আবাসভূমি অবশ্যই দরকার। উপমহাদেশের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলগুলো নিয়ে মুসলমানদের একটি পৃথক রাষ্ট্র হবে- যার নাম হবে পাকিস্তান।
প্রায় আট বছর প্রচণ্ড আন্দোলন ও সংগ্রামের পর ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তান নামে মুসলমানদের জন্যে একটি পৃথক রাষ্ট্রের জন্ম হয়। উপমহাদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ পাকিস্তান ও তথায় ইসলামী শাসনের দাবিতে অকাতরে জীবন দিল। লক্ষ লক্ষ নারী-শিশুর তাজা খুনে ধরণী রঞ্জিত হলো- ১৪ আগস্টের পর লক্ষ লক্ষ মানুষ খুনের দরিয়া সাঁতরিয়ে নবজাত পাকিস্তানের যমীনে পা দিল।
সকলের বুকভরা আশা- বহুকালের ইপ্সিত ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হতে যাচ্ছে। সকল অনাচার-অত্যাচার, আর্তনাদ, হাহাকার শোধ হয়ে যাবে। এক পরিপূর্ণ সত্য ও সুবিচারের সমাজ কায়েম হবে। মানুষে মানুষে বৈষম্য ও বিভেদের প্রাচীর ভেঙ্গে চুরমার হবে- লুটতরাজ, শোষণ-বঞ্চনা বন্ধ হয়ে যাবে। কুরআন ও সুন্নাহর আইনের অধীনে দুনিয়াতে নতুন করে এক স্বর্গীয় সমাজ গড়ে উঠবে।
কিন্তু হলো বিপরীত। লর্ড ক্রোমারদের কথাই অক্ষরে অক্ষরে প্রতিফলিত হলো। একে তো ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনার জন্যে কোন লোক তৈরি করা হয়নি এবং তার কোন পরিকল্পনাও ছিল না। অনেকে এ মারাত্মক ভুল ধারণা পোষণ করেছিলেন যে, ইসলামী রাষ্ট্র চালনার জন্যে তো শুধুমাত্র মুসলমান হওয়াই যথেষ্ট। আর কোন বৈশিষ্ট্যের কোন প্রয়োজন নেই। এই চিন্তা-ধারণা একেবারে ভুলই প্রমাণিত হয়েছে।
তার কারণ উপমহাদেশে ব্রিটিশ কর্তৃক প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতি মুসলমানদেরকে ইসলামের শাশ্বত বিধানের সম্পূর্ণ বিপরীত মুখে ঠেলে দিয়েছে। গড্ডালিকা প্রবাহে ভেসে যাওয়াই যে জাতির শিক্ষানীতি, তাদের নৈতিক মেরুদণ্ড কখনো মজবুত হতে পারে না। ইসলাম আমাদেরকে এ কথাই শিক্ষা দেয় যে, স্রোতের গতি যেদিকে এবং যে মুখেই হোক না কেন, সর্বাবস্থায় খুব দৃঢ়তার সাথে আমাদেরকে শুধু আল্লাহ নির্ধারিত পথেই চলতে হবে। একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব লাভ করেও তাকে ইসলামের আদর্শ অনুযায়ী পরিচালিত করা সেকিউলার বা ধর্মহীন শিক্ষাব্যবস্থার অধীনে তৈরি নেতৃবৃন্দের পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়। কারণ ইসলামী রাষ্ট্রে পুলিশ, আদালত, সেনাবাহিনী, প্রশাসনিক ও শিক্ষা বিভাগ, অর্থনীতি ও পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনার জন্যে যে ধরনের মন-মানসিকতা এবং চারিত্রিক শক্তিসম্পন্ন লোকের দরকার তা তৈরি করার কোন ব্যবস্থাই করা হয়নি। প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার অধীনে যে ধরনের শিক্ষা দেয়া হয়েছে, তা একটা অনৈসলামী বা তাগুতী রাষ্ট্রের জন্যে রাষ্ট্রপ্রধান থেকে শুরু করে সর্বস্তরের দায়িত্বশীল সংগ্রহ করে দিতে পারতো একথা ঠিক। কিন্তু তা ইসলামী রাষ্ট্রের জন্যে একজন চাপরাশি বা ইসলামী পুলিশ বিভাগের একজন সাধারণ সিপাই তৈরি করে দিতে পারে না।
দুঃখের বিষয় উপমহাদেশে অসংখ্য মাদ্রাসা, দারুল উলুম প্রভৃতি বিদ্যমান ছিল। কিন্তু আধুনিক যুগে ইসলামী রাষ্ট্রের জন্যে যে ধরনের বিচারপতি, বিভিন্ন বিভাগের সেক্রেটারি এবং রাষ্ট্রদূতের আবশ্যক, আমাদের প্রাচীন মাদ্রাসা শিক্ষা পদ্ধতি সে ধরনের একজন লোকও তৈরি করতে পারেনি। এমন অবস্থায় যারা মনে করতো যে, ‘মুসলমান’ নামক লোকদের হাতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা এলেই ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে, তাদের চিন্তা-ধারণা যে কত ভ্রান্ত ছিল তা প্রমাণিত হলো।
উপমহাদেশের স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইসলামী শাসন পরিচালনার লক্ষ্যে কোন লোক তৈরি করা হয়নি এবং মাদ্রাসা দারুল উলুমগুলোও এ কাজ করেনি। তার ফলে ক্রোমার সাহেবদের তৈরি লোকদের হাতেই দেশ পরিচালনার দায়িত্ব এলো। তারা সর্বশক্তি দিয়ে ইসলামের নামে তৈরি পাকিস্তানে ইসলাম আগমনের সকল পথ রুদ্ধ করে রাখলো।
পাকিস্তান হওয়ার পর কিভাবে তার শাসনভার ইংরেজদের তৈরি এ দেশীয় মুসলমান নামধারী লোকদের হাতে এলো তার সুন্দর বিবরণ দিয়েছেন- জনাব আলতাফ গওহর। তিনি ব্রিটিশ আমলেই চাকুরিতে যোগদান করেন এবং পরবর্তীকালে ষাটের দশক পর্যন্ত পাকিস্তান সরকারের অতি গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি বলেন-
ব্রিটিশ আমাদের শাসক মহলকে ঔপনিবেশিক স্বার্থ সংরক্ষণ ও বিশেষ ধরনের প্রতিষ্ঠান চালাবার দক্ষতা শিক্ষা দিয়েছিল। দেশীয় শাসকরা (Bureaucrats) মনে করে নিয়েছিলেন যে, পূর্ববর্তী শাসকদের প্রতিষ্ঠানগুলোর অস্তিত্বের সাথেই তাদের নিজেদের অস্তিত্ব জড়িত। স্বাধীনতা তাদেরকে পরোক্ষ প্রাধান্যের মর্যাদা থেকে সরাসরি শাসকের পদে অধিষ্ঠিত করে দিয়েছে। তাদের মতে পূর্বতন প্রতিষ্ঠানসমূহ ও সিস্টেম (ব্রিটিশ শাসন পদ্ধতি) অপেক্ষা আর কোন উত্তম ব্যবস্থা দেশের স্বার্থ রক্ষার জন্যে হতে পারে না।
আলতাফ গওহর আরও বলেন, তখন খাস ইংরেজরা ছিলেন আমাদের আদালতের জজ-ম্যাজিস্ট্রেট। আমাদের নতুন শাসকদের অন্ধ অনুকরণপ্রীতি দেখুন যে, ঐসব জজদের পরিবারে এদের বিয়ে-শাদী ও দাফন-কাফনের সুযোগ না থাকলেও তাদের এবং অ্যাংলো স্যাক্সনদের (Anglo-saxsons) রীতি-পদ্ধতি এরা অন্ধভাবে মেনে চলতেন। ঠিক তেমনি ব্রিটিশদের প্রচলিত শাসনপদ্ধতি ও অর্থব্যবস্থা থেকেও এক ইঞ্চি সরে যেতে এরা প্রস্তুত ছিলেন না।
পাকিস্তান হাসিলের জন্যে জনগণ সন্তুষ্টচিত্তে যথাসর্বস্ব কুরবানী করেছে এ জন্যে যে, তারা তাদের নিজস্ব আবাসভূমিতে আপন আকীদা-বিশ্বাস ও জীবনপদ্ধতি বাস্তবায়িত করবে। কিন্তু তারা বিক্ষুব্ধ, মর্মাহত ও নিরাশ হয়ে পড়লো। তাদের মনোবল একেবারে ভেঙ্গে গেল যখন তারা দেখলো যে, পাকিস্তান ইংরেজ শাসনের ধারাবাহিকতারই নামান্তর হয়ে পড়েছে।
দুনিয়ার কোথাও একমুহূর্তের জন্যে কোন স্বাধীন ইসলামী রাষ্ট্র ব্রিটিশ তথা জাহেলিয়াত বরদাশত করবে না তা আমরা লর্ড ক্রোমারের মুখে শুনলাম। দুনিয়ার সকল ইসলামবিরোধী শক্তি ইসলামী শাসনের বিরোধী, নতুন পাকিস্তানে যারা ক্ষমতায় এলো তারাও ইসলামী শাসনের বিরোধী। কিন্তু দেশের জনসাধারণ ও আলেম সমাজ ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রণয়ন ও ইসলামী শাসনের আন্দোলন করতে থাকে। এ আন্দোলনে নেতৃত্ব দান করে মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল আ’লা মওদূদী প্রতিষ্ঠিত জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তান। এ জামায়াতটি গঠিত হয় ১৯৪১ সালে। এ সময়ে সমগ্র এশিয়া-ইউরোপে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রলয় নাচন চলছিল। উপমহাদেশে একদিকে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস একজাতীয়তার ভিত্তিতে একটি সেকিউলার রাষ্ট্র গঠনের লক্ষ্যে ব্রিটিশের নিকট থেকে ক্ষমতা দখলের আন্দোলন করছিল এবং অপরদিকে মুসলমানগণ আন্দোলন করছিলেন তাদের জন্যে একটি পৃথক আবাসভূমি চিহ্নিত করে তথায় হুকুমতে ইলাহীয়া বা ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে; এমন সময়ে জামায়াতে ইসলামী নামে একটি দল গঠনের প্রয়োজনীয়তা কি- এ প্রশ্ন ছিল অনেকের মনে। এ প্রশ্নের সঠিক জবাব পেতে হলে যে হুকুমতে ইলাহীয়া বা ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্যে পাকিস্তান আন্দোলন চলছিল সে সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ করতে হবে।
হুকুমতে ইলাহীয়া তথা ইসলামী রাষ্ট্রের গোটা কাঠামো আল্লাহতায়ালার প্রভুত্ব কর্তৃত্বের বুনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত। বিশ্বজগতের স্রষ্টা, প্রভু ও বাদশাহ-আইনদাতা একমাত্র আল্লাহতায়ালা। এ হলো ইসলামী রাজনীতির মৌলিক ধারণা। কোন ব্যক্তি, পরিবার, গোষ্ঠী বা জাতির মানুষের উপর প্রভুত্ব বা শাসন করার কোন অধিকার নেই। সমগ্র সৃষ্টি যেহেতু আল্লাহতায়ালার সে জন্যে তার উপর হুকুম-শাসনের অধিকার একমাত্র তাঁরই। আর মানুষ তাঁর খলিফা বা প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করবে। একথা মানুষের সর্বদা স্মরণ রাখা দরকার যে, তার উপর যে আল্লাহর খিলাফত বা প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে, তা এজন্য নয় যে, সে অন্যান্য মানুষের প্রভু হয়ে বসবে- তাদেরকে তার দাসানুদাস বানিয়ে রাখবে, তাদের প্রভু সেজে নিজের লালসা ও পাশবিক বৃত্তি চরিতার্থ করবে। বরঞ্চ প্রকৃতপক্ষে খিলাফতের দায়িত্ব তার উপর এ জন্যে অর্পিত হয়েছে যে, সকলে মিলে আল্লাহর বান্দাদের উপর আল্লাহরই আইন জারি করবে। নিজেরাও পুরোপুরি সে আইন মেনে চলবে। তাদের মধ্যে এ বিশ্বাসও সর্বদা জাগ্রত থাকবে যে, আল্লাহর আইন অন্যের উপর জারি করতে কোন প্রকার অবহেলা বা ত্রুটি করলে, অথবা সামান্য স্বার্থপরতা, স্বেচ্ছাচারিতা, হিংসা-বিদ্বেষ, পক্ষপাতিত্ব বা বিশ্বাসঘাতকতা করলে এ দুনিয়ার জীবনে তার কোন বিচার না হলেও পরকালে আল্লাহর আদালতে তাকে অবশ্যই শাস্তি পেতে হবে।
উপরের আদর্শ, বিশ্বাস ও ভাবধারা-ভিত্তিতে যে রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েম হয় তাকেই বলে ইসলামী রাষ্ট্র এবং তা মূল থেকে শুরু করে শাখা-প্রশাখা পর্যন্ত প্রত্যেকটি বিভাগই ধর্মহীন রাষ্ট্র (Secular State) থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর হয়ে থাকে। অন্য কোন রাষ্ট্রব্যবস্থার সাথে তার কোন তুলনাই হতে পারে না। তার সেনাবাহিনী, পুলিশ, আদালত, রাজনীতি, অর্থনীতি, যুদ্ধ ও সন্ধি তৎসংক্রান্ত নীতি ও কার্যকলাপ প্রভৃতি ধর্মহীন রাষ্ট্র থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। সেকিউলার রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ দায়িত্বশীল ব্যক্তি ইসলামী রাষ্ট্রের কোন সামান্য পদ লাভের যোগ্যও হতে পারে না। ইসলামী রাষ্ট্রের একটি বিভাগ ও পদের জন্যে এমন সব নিঃস্বার্থ লোকের প্রয়োজন যাদের ধনদৌলতের লালসা ও ভোগ-বিলাসের কোন লিপ্সা থাকবে না। তারা হবে অত্যন্ত বিশ্বস্ত ও আমানতদার। প্রতিটি কাজ সম্পাদন করবে পূর্ণ দায়িত্বানুভূতির সাথে। বিপুল ধনভাণ্ডার হস্তগত হলেও একটি কপর্দকও আত্মসাৎ করবে না। তারা তাদের দায়িত্ব সঠিকভাবে ও সততার সাথে পালন করছে কিনা তার জন্যে আখিরাতে আল্লাহর দরবারে জবাবদিহি করতে হবে- এ অনুভূতি তাদের মনে সর্বদাই জাগ্রত থাকে। জাহেলিয়াতের কোন চিন্তা-ধারণা তাদের মন-মস্তিষ্ক আচ্ছন্ন করতে পারে না।
কিন্তু প্রস্তাবিত বা ইপ্সিত ইসলামী রাষ্ট্রের জন্যে এ ধরনের কোন কর্মীবাহিনী তৈরি করা হয়েছে কি, অথবা তৈরি করার কোন পরিকল্পনা আছে কি?
জামায়াতে ইসলামী গঠনের পূর্বে এর প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল আ’লা মওদূদী মুসলিম সমাজের মর্মান্তিক নৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থার চিত্র তুলে ধরে বলেন-
“ভালোমন্দ সকল প্রকার লোকই এ সমাজে বর্তমান। চরিত্রের দিক দিয়ে যত প্রকারের মানুষ দুনিয়ায় অমুসলিম জাতিগুলোর মধ্যে পাওয়া যায়, ঠিক তত প্রকারের মানুষ এ মুসলিম নামধারী জাতির মধ্যে বিদ্যমান। আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়ার ব্যাপারে একজন অমুসলিম যতোখানি সক্ষম, একজন মুসলমানও তার চেয়ে কোন অংশে কম নয়। সুদ-ঘুষ, চুরি-ডাকাতি, ব্যভিচার, মিথ্যাবাদিতা, ধোঁকা-প্রতারণা এবং অন্যান্য সকল প্রকার অপরাধ অমুসলিমগণ যে হারে করে, মুসলমানগণ তাদের চেয়ে কিছুমাত্র কম করে না। বিশেষ স্বার্থলাভ এবং অর্থ উপার্জনের জন্যে কাফিরগণ যেসব কৌশল অবলম্বন করে, মুসলমানগণও সে সব করতে কুণ্ঠিত হয় না। মুসলিম আইন ব্যবসায়ী জেনে বুঝে প্রকৃত সত্যের বিরুদ্ধে ওকালতি করে। সে মুহূর্তে একজন অমুসলিম আল্লাহকে যতোখানি ভুলে যান, একজন মুসলিম আইন ব্যবসায়ীও ততোখানি ভুলে যান। ....যে জাতির নৈতিক অবস্থা এতো হীন ও অধঃপতিত, তার সে নানা মতের ও নানা প্রকৃতির বিরাট ভিড় জমিয়ে একটি বাহিনী গঠন করে দিলে অথবা রাজনৈতিক শিক্ষা-দীক্ষার মাধ্যমে তাদেরকে শৃগালের চেয়ে চতুর করে তুলতে পারলে অথবা যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী করে তাদের মধ্যে ব্যাঘ্রের হিংস্রতা সৃষ্টি করে দিলে অরণ্যজগতের হয়তো প্রভুত্ব করা সহজ হতে পারে। কিন্তু তার সাহায্যে ইসলামী শাসন কায়েম হওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। কারণ এমতাবস্থায় কেউই তাদের নৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করবে না, কারো দৃষ্টি তাদের সামনে শ্রদ্ধায় অবনমিত হবে না। তাদের দেখে কারো মনে ইসলামের আবেগময়ী ভাবধারা ও অনুপ্রেরণা জাগ্রত হবে না এবং এসব কারণেই ইসলামের সীমার মধ্যে দুনিয়ার মানুষের দলে দলে প্রবেশের মনোমুগ্ধকর দৃশ্য দেখার ভাগ্য কখনোই হবে না।”
মাওলানা আরও বলেন, “এ ধরনের লোকদের হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা ন্যস্ত হওয়ার ফলে একটা স্বাধীন রাষ্ট্র লাভ করার পরও আমরা ঠিক সে অবস্থায়ই জীবন যাপন করতে বাধ্য হবো, যে অবস্থায় ছিলাম স্বাধীনতা লাভের পূর্বে একটি অমুসলিম রাষ্ট্রের অধীনে। বরঞ্চ তার চেয়েও নিকৃষ্ট ও মারাত্মক পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে। কারণ যে ধরনের রাষ্ট্রের উপর ‘ইসলামী রাষ্ট্র’-এর লেবেল লাগানো থাকবে তা ইসলামী বিপ্লবের পথ রোধ করার ব্যাপারে অমুসলিম রাষ্ট্র অপেক্ষাও অধিকতর সাহসী ও নির্ভীক হবে। এমনকি একটি অমুসলিম রাষ্ট্র যেসব অপরাধের দরুন কারাদণ্ড দেবে, এ ‘মুসলিম জাতীয় রাষ্ট্র’ সেসব ক্ষেত্রে প্রাণদণ্ড অথবা নির্বাসন দণ্ড দেবে।”
সূক্ষ্মদর্শী ও দূরদর্শী মাওলানার এসব ভবিষ্যদ্বাণী পাকিস্তানে অক্ষরে অক্ষরে প্রতিফলিত হতে দেখা গেছে। ১৯৪৭-এর পর থেকে এ যাবত পর্যন্ত সেখানে ইসলাম ও জাহেলিয়াতের মধ্যে প্রচণ্ড দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ চলতেই আছে। ইসলাম এখনও বিজয়ী শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি।
এখন জামায়াতে ইসলামী কেন গঠন করা হয়েছিল- এ প্রশ্নের জবাব অতি সহজেই পাওয়া যাবে। আন্দোলনের ফলে পাকিস্তান নামে একটি দেশ হয়তো লাভ করা যাবে। সে দেশকে দ্বিতীয় তুরস্ক হওয়া থেকে রক্ষা করার জন্যে এবং দেশ বিভক্তির পর অনিবার্যরূপে ভারতে রয়ে যাওয়া চার-পাঁচ কোটি মুসলমানকে রক্ষা করার জন্যে একটি মজবুত আদর্শবাদী ইসলামী জামায়াত গঠন অপরিহার্য। এ উদ্দেশ্যে দলটি গঠিত হয় এবং ১৯৪১ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত অন্য সকল প্রকার কর্মতৎপরতা থেকে মুখ ফিরিয়ে দলটি তার কর্মী বাহিনীকে নিরিবিলি প্রশিক্ষণ দিতে থাকে যেন সকল ইসলামবিরোধী তৎপরতার মুকাবিলা করতে পারে, এবং ইপ্সিত পাকিস্তানকে সত্যিকার অর্থে একটি ইসলামী রাষ্ট্র বানাবার প্রাণপণ সংগ্রাম করতে পারে।
পাকিস্তানের বিগত কয়েক যুগের ইতিহাস এ কথার সাক্ষ্য বহন করে যে, যে উদ্দেশ্যে জামায়াতে ইসলামী গঠিত হয়েছিল সে উদ্দেশ্যেই সে পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকে এ যাবত সংগ্রাম করে এসেছে এবং এখনও করছে।
পাকিস্তান রাষ্ট্র জন্মলাভের পর জাহেলিয়াত তার পরিপূর্ণ রূপ ও অবয়বসহ আত্মপ্রকাশ করতে থাকে। বিগত সাত বছর জামায়াত যে কাজের প্রশিক্ষণ নিয়েছিল কিন্তু যে কাজ তার করতে হয়নি, এখন সে কাজে সে আত্মনিয়োগ করলো। জাহেলিয়াত-সর্পের উত্তোলিত ফণা অবদমিত ও তার গতিরোধ করে সর্বশক্তি দিয়ে ইসলামী আন্দোলন শুরু করে জামায়াতে ইসলামী। জাহেলিয়াতের পতাকাবাহীগণ যে পাকিস্তানকে তুরস্কের মতো একটি সেকিউলার বা ধর্মহীন রাষ্ট্র বানাতে বদ্ধপরিকর ছিলেন, ইসলামী আন্দোলনের প্রবল চাপে ১৯৪৯ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি, ইসলামী শাসনের মূলনীতি হিসেবে ঐতিহাসিক আদর্শ প্রস্তাব গ্রহণ করতে তারা বাধ্য হন। এ তাদের করতে হয়েছে ইচ্ছার বিরুদ্ধে গণআন্দোলনের চাপে। এ জন্যে শাসকগোষ্ঠীর সকল ক্রোধ-আক্রোশের শিকার হয়ে পড়েন ইসলামী আন্দোলনের নেতা মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল আ’লা মওদূদী। ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে তাঁর বিরুদ্ধে অমূলক অভিযোগ আরোপ করে সামরিক আদালতে বিচারের প্রহসন করা হয় এবং তাঁর প্রতি মৃত্যুদণ্ডাদেশ প্রদান করা হয়। জাহেলিয়াত মনে করেছিল ইসলামের মহান নেতাকে ধরাপৃষ্ঠ থেকে অপসারিত করতে পারলে জাহেলিয়াতের পথ রোধ করার সাধ্য আর কারো হবে না। কিন্তু জাহেলিয়াতকে পরাজিত ও লাঞ্ছিত হতে হয়েছে। মাওলানার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা যায়নি। বরঞ্চ তাঁর স্বাভাবিক মৃত্যুর বহু পূর্বে জাহেলিয়াতের পতাকাবাহীদেরকে অতীব লাঞ্ছনার মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে। কিন্তু তারপরও ইসলাম ও জাহেলিয়াতের দ্বন্দ্ব ও জয়-পরাজয় চলতেই থাকে এবং এখনও চলছে।
ইসলাম ও জাহেলিয়াতের এ দ্বন্দ্ব-সংগ্রামে অন্য এক বেদনাদায়ক যে চিত্রটি ফুটে উঠে তা এই যে, কতিপয় বুযর্গানে দ্বীন বলে পরিচিত ও স্বীকৃত ব্যক্তি তাদের আচরণে ইসলামের পরিবর্তে জাহেলিয়াতের হাতকেই মজবুত করে দিয়েছেন। ইসলামী আন্দোলনের নেতার বিরুদ্ধে নানান ধরনের অমূলক ও ভিত্তিহীন অভিযোগ রচনা করা হতে থাকে এবং ফতোয়াবাজির মেশিনগান থেকে ঘন ঘন ফতোয়ার গোলাবর্ষণ হতে থাকে। বহুবিধ অভিযোগের সাথে এ অভিযোগও করা হয় যে, ইসলামী আন্দোলনের নেতা ও তাঁর দল ইলমে তাসাওউফে বিশ্বাসী নন। রূহানিয়াত বলে কোন জিনিসও তাদের মধ্যে নেই এবং সেই সাথে তাকওয়ার ভয়ানক অভাব। এমনকি আন্দোলনের নেতাকে পথভ্রষ্ট এবং ইহুদী-কাদিয়ানী থেকে নিকৃষ্ট বলে অভিহিত করা হয়। কিন্তু জাহেলিয়াতের বিরুদ্ধে একটি শব্দও তাদের মুখ থেকে বেরোয়নি।
ইসলামপন্থী জনগণ এবং বিশেষ করে তাসাওউফপন্থী মুসলমানগণের অনেকেই উপরোক্ত প্রচারণায় বিভ্রান্ত হয়েছেন এবং ইসলামী আন্দোলনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়েছেন। এ নিয়ে বিভিন্ন মহলে নানান আলাপ-আলোচনা এবং কল্পনা-জল্পনাও চলেছে। অনেকে অনুভব করছিলেন যে, বিষয়টির ইসলামসম্মত ও বুদ্ধিবৃত্তিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ প্রয়োজন। ফলে প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটিত হবে এবং সকল বিভ্রান্তি দূর হয়ে যাবে বলে আশা করা যায়। এখন দেখা যাক এ বিষয়ে ইসলামী আন্দোলনের নেতা কিছু আলোকপাত করেছেন কিনা।
তাযকিয়ায়ে নফস (তাসাওউফ) ও রূহানিয়াত
শতাব্দীর অন্যতম ইসলামী চিন্তাবিদ ও মুজাহিদ সাইয়্যেদ আবুল আ’লা মওদূদী বিষয়টির পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনা করে যে বিজ্ঞ অভিমত প্রকাশ করেন তা নিঃসন্দেহে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন-
“কয়েক শতাব্দীর অধঃপতন ও বিকৃতির ফলে মুসলমানদের মধ্যে যেখানে বহুবিধ পরিবর্তন সূচিত হয়েছে, সেখানে তাযকিয়ায়ে নফস (আধ্যাত্মিক আত্মশুদ্ধি)-এর ব্যাপারেও তাদের ধারণা প্রকৃত ইসলামী ধারণা থেকে অনেকটা ভিন্নতর হয়েছে। তাদের উদ্দেশ্যও বদলে গেছে, দৃষ্টিকোণও সীমিত হয়েছে এবং ‘তাযকিয়ায়ে নফসে’র নিয়ম-পদ্ধতিও সেসব নিয়ম-পদ্ধতি থেকে ভিন্নতর হয়ে পড়েছে যা নবীযুগে অবলম্বন করা হয়েছিল। তার ফল এই হয়েছে যে, যেসব বিরাট বিরাট প্রতিষ্ঠান এবং বুযর্গানে দ্বীনের তা’লিম ও তরবিয়তের সিলসিলা যুগ যুগ ধরে কায়েম আছে তার বরকতে বিরাট বিরাট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষও তৈরি হয়েছেন। কিন্তু সে ধরনের গুণসম্পন্ন লোক এখনো তৈরি হতে পারেননি, যাঁরা জাহেলিয়াতের পথে জগত পরিচালনাকারী বিরাট শক্তির মুকাবিলায় দাঁড়াবেন এবং তার বিরুদ্ধে শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়ে ইসলামকে দুনিয়ায় নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বশীল দ্বীন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করবেন। এ তো এক বিরাট কাজ। এখানে তো নিদেনপক্ষে এমন একজন লোকও তৈরি হলেন না যিনি অন্ততঃ এতোটুকু করতে পারতেন যে, ইসলামের প্রভাবাধীন পরিমণ্ডলে জাহেলিয়াতের অগ্রগতিকে বাধাদান করতেন। বিরাট বিরাট পূতঃচরিত্র মহান ব্যক্তিত্ব বিদ্যমান ছিলেন এবং এখনো আছেন। তাঁরা তাঁদের ইলম ও আমল, দিয়ানতদারী, পরহেজগারী এবং নিজেদের নিষ্কলুষ জীবনের জন্যে অবশ্যই প্রশংসার পাত্র। কিন্তু এসব মহান ব্যক্তির উপস্থিতিতেই জাহেলিয়াত তার তলোয়ারের সাহায্যে, তার লেখনীর সাহায্যে, তার জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পকলার সাহায্যে এবং তার সভ্যতা-সংস্কৃতির সাহায্যে শুধু দুনিয়াকে নয়, বরঞ্চ মুসলমান দেশ ও জাতিকে পরাভূত করে চলেছিল এবং এখনো চলছে। এ দুর্বলতার কারণ তো অবশ্যই থাকার কথা। আর যে কোন কারণই থাক না কেন, কারো প্রতি অসঙ্গত ও অযৌক্তিক শ্রদ্ধাবোধ সে কারণ নির্ণয়ে প্রতিবন্ধক না হওয়াই উচিত।
আমাদের এখানে একটি মহলের নিকটে ‘তাযকিয়ায়ে নফসের’ উদ্দেশ্য ছিল এই যে, এ জীবনেই যেন সত্য পর্যবেক্ষণের নসীব হয়ে যায়। ঈমান বিল গায়েবের মকাম অতিক্রম করে যেন ঈমান বিশ-শাহাদাতের দৌলত হাসিল করা যায়। দৃশ্যতঃ এ একটি অতি মহান ও পবিত্রতম উদ্দেশ্য। কিন্তু কুরআন কোথাও আমাদেরকে এ শিক্ষা দেয়নি যে, আমরা তাকে উদ্দেশ্য বলে গণ্য করে এ পথে আমাদের চেষ্টা চরিত্র চালাতে থাকব। ঠিক এর বিপরীত, আমরা যদি তাকে আমাদের উদ্দেশ্য বলে গণ্য করিও, কুরআন আমাদেরকে এ নিশ্চয়তা দান করে যে, এ জীবনে নবী ব্যতীত এ সম্পদ আর কেউ লাভ করতে পারবে না।
কুরআনে বলে-
তিনি (আল্লাহ) গায়েবের জ্ঞান রাখেন। তাঁর গায়েব তিনি কারো কাছে প্রকাশ করেন না। (অবশ্যি) সেই রসূল ব্যতীত যাকে তিনি (গায়েবী কোন জ্ঞানদানের জন্যে) পছন্দ করে নিয়েছেন। তখন তার সম্মুখে ও পেছনে পাহারা দেয়ার জন্যে তিনি ফেরেশতা নিযুক্ত করেন- এটা জানার জন্যে যে, তারা তাদের খোদার পয়গামসমূহ পৌঁছিয়ে দিয়েছে- (সূরা জ্বিনঃ ২৬-২৮)।
এর থেকে জানা গেল যে, অদৃশ্য পর্দার মধ্যে লুক্কায়িত প্রকৃত তথ্যাবলী অন্য কথায় অতিপ্রাকৃতিক তথ্যাবলী পর্যবেক্ষণের চেষ্টা অনাবশ্যকও এবং ভুলও। এর সাফল্যের কোন সম্ভাবনা নেই। এসব তথ্যাবলীর যতটুকু এবং যত পরিমাণ জ্ঞান মানুষের প্রয়োজন ছিল, আল্লাহতায়ালা সে জ্ঞান তার রসূলগণের মাধ্যমে দান করেছেন। আর এ আল্লাহতায়ালার বিরাট ইহসান যে, এভাবে তিনি মানুষকে এসব অনুসন্ধানের কষ্ট থেকে রক্ষা করেছেন। এখন মানুষের কাজ শুধু এই যে, সে রসূলগণের দেয়া জ্ঞানের ভিত্তিতে ঈমান বিল গায়েব পোষণ করবে এবং যে দায়িত্ব তার উপর আরোপিত তা সন্তুষ্টচিত্তে আঞ্জাম দেয়ার কাজে লেগে যাবে।
এর চেয়ে নিম্নতর স্তরের ‘তাযকিয়ায়ে নফসের’ যে উদ্দেশ্য বলা হয়, তা হলো ‘রূহানী’ উন্নতি। কিন্তু এ ‘রূহানী উন্নতি’ এমন দ্ব্যর্থবোধক ও রহস্যপূর্ণ যে, সারাজীবন আলেয়ার আলোর পেছনে ছুটে বেড়ানোর পরও মানুষ কিছুই জানতে পারে না যে, সে কোন মকামে পৌঁছেছে। এর পরিভাষা, এর স্তরসমূহ এবং এর ফলাফল সবই রহস্যাবৃত যা আমাদের মতো সাধারণ মানুষের কাছে অবোধগম্য। আমরা যা কিছু দেখতে পাই তা হলো এই যে, এর পথে যেসব স্তর অতিক্রম করা হয় সেসবের মধ্যে সে স্তর কখনো আসে না যা বেলাল (রা), আম্মার (রা) এবং সুহাইব (রা) অতিক্রম করেছিলেন। আর না সে স্তর কখনো আসবে বলে আশা করা যায়, যা আবু বকর (রা) এবং ওমর (রা) অতিক্রম করেছিলেন।
যারা ‘তাযকিয়ায়ে নফস’ থেকে ‘তাকওয়া’ হাসিল করতে চান, ইসলামের উদ্দেশ্যের নিকটতম উদ্দেশ্য তাদের। কিন্তু এখানে বিপদ এই যে, তাকওয়া সম্পর্কে সাধারণতঃ মানুষের দৃষ্টিকোণ বড়ো সীমিত হয়ে রয়ে গেছে। অধিকাংশ বুযর্গানের কাছে তাকওয়া বলতে বুঝায় লেবাসপোশাক, তার বিশেষ ধরন, ওঠাবসা, পানাহার প্রভৃতি ব্যাপারে এমন প্রকাশ্য নকশায় জীবনকে ঢেলে সাজানো যার খুটিনাটি বিষয় হাদিসসমূহে বয়ান করা হয়েছে। উপরন্তু কিছু মাযহাবী ক্রিয়াকর্ম নিয়মিত পালন করে চললে এবং চিরাচরিত অভ্যাস থেকে বেশি বেশি ইবাদাত-বন্দেগী করলে তাকওয়ার পরিপূর্ণতা লাভ করা যায়। এর ফল এই যে, যারা তাকওয়ার এ প্রকাশ্য আকার-আকৃতি অবলম্বন করেছেন, তাদেরকে মুত্তাকী বলা হয় এবং মনে করা হয়। তারাও নিশ্চিন্ত হয়ে যান যে, তারা নিজেদের মধ্যে তাকওয়া পয়দা করে নিয়েছেন। বস্তুতঃ প্রকৃতপক্ষে তাদের মধ্যে তাকওয়ার বিরাট অভাব থাকে এবং অধিকাংশ সময়ে বাস্তব জীবনের বিভিন্ন অগ্নিপরীক্ষায় এমন এমন তাকওয়াবিরোধী আচরণ তাদের দ্বারা হয়ে যায় যার কারণে তাকওয়ার সে প্রকাশ্য আকার-আকৃতির মর্যাদাও বিনষ্ট হয়। তাকওয়ার এ সাধারণ ধারণা থেকে উচ্চতর ও ব্যাপকতর যে ধারণা বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিবর্গের মধ্যে পাওয়া যায়, তাও এর চেয়ে বেশি নয় যে, ব্যক্তিগত জীবনে মানুষ খোদাভীরু, ইবাদাতগুজার এবং যিকিরকারী ও শোকরকারী হবে। কাজ-কারবারে বিশ্বস্ততা, সততা এবং আল্লাহর সীমারেখা অবলম্বন করে চলবে। সেইসাথে সমাজে অন্যান্য লোকের সাথে সদাচার, সহানুভূতি, ভ্রাতৃত্ব, সুবিচার এবং অধিকার পৌঁছিয়ে দেয়ায় পন্থা-পদ্ধতি মেনে চলবে। কিন্তু এ সীমিত ধারণায় ব্যাপকতর সামাজিক সামষ্টিক সমস্যাবলী উপলব্ধি করার কোন সুযোগ নেই। এজন্যে আমাদের অতি নেক লোকদের মধ্যেও যে ‘তাযকিয়ায়ে নফস’ করা হয়, তার সুফল এর চেয়ে বেশি কিছু হয় না যে, খোদাদ্রোহী সরকারগুলোর জন্যে খোদাভীরু প্রজা এবং ধর্মভীরু কর্মচারি সরবরাহ করা হয়। স্বয়ং এসব সরকারের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যেসব প্রজা ও কর্মচারি সরবরাহ করা হয় তাদের মধ্যে অন্যান্য যোগ্যতা তো থাকে, কিন্তু ঈমানদারি ও সততা থাকে না। সেজন্যে তারা সরকারের বড়ো ক্ষতিসাধনও করে। এ অভাব পূরণ করা হয় আমাদের ‘তাযকিয়ায়ে নফসের’ প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে। কুফরি শক্তির আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্যে সংগ্রাম করার এবং কুফরি শাসন চালাবার জন্যে এসব প্রতিষ্ঠান সত্যনিষ্ঠ লোক তৈরি করে এবং কুফরি শাসনের জন্যে এমন সব প্রজা তৈরি করে যারা তাদের জন্যে খুব কমই উদ্বেগের কারণ হয়। এমনকি আমাদের এখানে যদি কোন ব্যক্তি প্রকাশ্যে খোদাহীন ব্যবস্থা কায়েমের জন্যে আত্মনিয়োগও করে তথাপি সে অবিকল মুত্তাকীই রয়ে যায়। তবে শর্ত এই যে, উপরে বর্ণিত তাকওয়ার খুটিনাটি বিষয়গুলো তার জীবনে যেন পাওয়া যায়। এ হচ্ছে অনিবার্য ফল সে সীমিত ধারণার যা তাকওয়া এবং তাযকিয়ায়ে নফস সম্পর্কে আমাদের ধর্মীয় মহলে আম-খাস নির্বিশেষে সকলের মধ্যে ছড়িয়ে আছে”- (তরজুমানুল কুরআন, জুলাই-আগস্ট, ১৯৫৩)।
মানবজীবনের উপর সেকিউলারিজমের প্রভাব
‘সেকিউলারিজম’ দৃশ্যতঃ একটি সাদাসিধে ধারণা-মতবাদ হলেও তা এখন একটি সার্বিক জীবনদর্শনে পরিণত হয়েছে যা মানবজীবনের উপরে সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করে এবং গোটা জীবনকে এক নতুন ছাঁচে ঢেলে সাজায়। তার কিছু বুনিয়াদী প্রভাব-প্রতিক্রিয়া আলোচনা করা যাক। ‘সেকিউলারিজম’ তথা ধর্মহীনতার প্রথম অনিবার্য কুফল হচ্ছে এই যে, এ মানুষকে লাগামহীন স্বাধীনতা দান করে এবং কোন ঊর্ধ্বতন শক্তির কাছে জবাবদিহির অনুভূতি বিলুপ্ত করে দেয়। এ দায়িত্বহীনতার মানসিকতা ব্যক্তি ও জাতির প্রতি সমভাবে প্রযোজ্য। কোন শক্তিধর ব্যক্তি অথবা জাতি যদি মানবসমাজে জুলুম ও অনাচার সৃষ্টি করে মানুষের জীবন দুর্বিষহ করে তোলে, তাহলে কোন শক্তি তাদেরকে এর থেকে বিরত রাখতে পারে? কতিপয় ব্যক্তি ও জাতি ক্ষমতামদমত্ত হয়ে সাধারণতঃ দুর্বল মানুষ ও জাতির রক্তে হাত রঞ্জিত করছে। কারণ এ ধারণা তাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল যে, এর জন্যে তাদেরকে কারো কাছে জবাবদিহি করতে হবে না। সর্বশক্তিমান খোদার অস্তিত্ব যদি মেনে নিতে হয়, যিনি প্রতিটি মানুষ বা জাতির কর্মকাণ্ডের পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব নেবেন এবং পুরস্কার বা শাস্তি দেবেন তাহলে ‘সেকিউলারিজম’ দর্শনের ভিত্তিই তো ধসে পড়ে। খোদা ও আখিরাত থেকে বেপরোয়া করাই তো ‘সেকিউলারিজম’-এর কাজ। অতএব এ দর্শনের মূলকথা হলো- (MIGHT IS RIGHT, SURVIVAL OF THE FITTEST) অর্থাৎ জোর যার মুল্লুক তার। জোর করে কোনকিছু হস্তগত করাই ন্যায়সঙ্গত। তার জন্যে কারো কাছে জবাবদিহি করতে হবে না। ন্যায়-অন্যায়ের প্রশ্ন অবান্তর। আর যে সবচেয়ে শক্তিশালী, সে-ই প্রতিষ্ঠা লাভ করবে- তা অন্যায়ভাবেই হোক না কেন। আর দুর্বল যতোই ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত হোক, তার বেঁচে থাকার কোন অধিকার নেই।
আধুনিক জগতে ‘সেকিউলারিজমের’ এ দর্শনই সর্বত্র কার্যকর দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের ও তাহজিব-তামাদ্দুনের প্রভূত উন্নতি-অগ্রগতি সাধিত হওয়া সত্ত্বেও ধর্মবিবর্জিত মানুষ (SECULAR MAN) ক্ষমতালিপ্সু ও রক্তপিপাসু হয়ে পড়েছে- যার ফলে মানুষে মানুষে জাতিতে জাতিতে যুদ্ধ-বিগ্রহের অনির্বাণ অনল শিখা প্রজ্জ্বলিত করে রাখা হয়েছে যার থেকে দুনিয়া এখনো অব্যাহতি লাভ করতে পারেনি। লীগ অব নেশনস এবং ইউএনও (জাতিসংঘ) উভয়েই যুদ্ধের উন্মাদনা বন্ধ করতে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছে। কারণ সংশ্লিষ্ট জাতিসমূহ বিশেষ করে শক্তিশালী জাতিসমূহ দায়িত্বানুভূতি থেকে মুক্ত। কারণ কোন শক্তিমান সত্তার কাছে জবাবদিহি করতে হবে- এ বিশ্বাসই তারা পোষণ করে না। এর ফলে দুনিয়ার বুক থেকে মজলুম মানুষ ও জাতির আর্তনাদ-হাহাকার কোনদিন বন্ধও হতে পারে না।
‘সেকিউলারিজমের’ দ্বিতীয় কুফল প্রবৃত্তির দাসত্ব। প্রবৃত্তির দাসত্ব বা প্রবৃত্তিপূজা চরিত্রহীনতারই বুনিয়াদ এবং সকল দুষ্কৃতির মূল কারণ। প্রবৃত্তির অতৃপ্ত লালসা-বাসনা মানুষকে কুপথে পরিচালিত করে- যদি এ পথে কোন প্রতিবন্ধক শক্তি না থাকে। তখন সমাজে নানান অশান্তি-অনাচার দানা বাধে।
প্রবৃত্তির এ অতৃপ্ত লালসা-বাসনা মানুষকে পশুত্বের নিম্ন পর্যায়ে ঠেলে দেয় এবং এ লালসা চরিতার্থ করতে গিয়ে ব্যক্তি ও জাতির রক্তে হাত রঞ্জিত করতে হয়, শিশু ও নারী-পুরুষের আর্তনাদে আকাশ-বাতাস মথিত হয়। প্রবৃত্তির লালসা-বাসনা পূরণের পথে একমাত্র প্রতিবন্ধক শক্তি খোদার ভয় এবং আখিরাতে তার কাছে জবাবদিহির তীব্র অনুভূতি। এ খোদার ভয় ও জবাবদিহির অনুভূতি প্রতি মুহূর্তে অশরীরি এক পুলিশের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে মানুষকে দুষ্কর্ম থেকে বিরত রাখে। কিন্তু ‘সেকিউলারিজম’ যেহেতু সর্বত্র প্রতি মুহূর্তে খোদার ‘হাজির ও নাজির’ (সর্বদ্রষ্টা হিসেবে বিদ্যমান) থাকার, মানুষের গোপন ও প্রকাশ্য প্রতিটি কর্মেরও প্রত্যক্ষ জ্ঞান রাখার বিশ্বাস, তাঁর ভয় এবং তাঁর কাছে জবাবদিহির অনুভূতি মানুষের মন থেকে মুছে ফেলে দিয়েছে, সে জন্যে মানবসমাজ থেকে অনাচার-অবিচার, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, হত্যা, লুটতরাজ প্রভৃতি পাপাচার দূর করার আর কোন উপায় নেই।
উল্লেখ্য যে, জীবনের সকল স্তর থেকে বিশেষ করে শিক্ষা ব্যবস্থার প্রাথমিক স্তর থেকে সকল স্তর পর্যন্ত খোদা ও ধর্মকে বর্জন করে সেকিউলার শিক্ষাব্যবস্থা কায়েম করার ফলে যুবসমাজের মধ্যে অস্বাভাবিক অপরাধপ্রবণতা বেড়ে গেছে এবং এমন সব অপরাধ সংঘটিত হচ্ছে যা স্মরণ করতে শরীর রোমাঞ্চিত হয়। মানবসমাজ আতংকগ্রস্ত হয়। অতি অপরিমিত বয়সেই তরুণ-তরুণী ও যুবক-যুবতী যৌন অপরাধ ও তজ্জনিত হত্যাকাণ্ড, চুরি-ডাকাতি, ছিনতাই ও লুটতরাজে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। একই কারণে পরীক্ষায় নকল প্রবণতার ব্যাধি তাদের মধ্যে প্রকট আকার ধারণ করছে। এ সবকিছুই সেকিউলারিজমের মারাত্মক কুফল।
সেকিউলারিজমের তৃতীয় কুফল স্বার্থপরতা ও সুবিধাবাদ। এ এক অনস্বীকার্য সত্য যে, মানুষের শ্রম সাধনা, চেষ্টা-চরিত্র ও জীবনের একটি উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অবশ্যই থাকা উচিত। খোদা ও আখিরাতের প্রতি যারা বিশ্বাসী, তাদের জীবনের উদ্দেশ্য হলো আল্লাহতায়ালার সন্তুষ্টি এবং সকল চেষ্টা-চরিত্রের লক্ষ্য আখিরাতের সাফল্য ও মুক্তি। আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আখিরাতের সাফল্য- এ দু’টি বস্তুর উপর তাদের সকল দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে। দুনিয়ার নগণ্য ও ক্ষণস্থায়ী স্বার্থের পরিবর্তে তারা আখিরাতের বিরাট ও চিরন্তন সাফল্যের প্রতিই অনুরক্ত হয়। তারা দুনিয়ার সাথে ততোটুকু সম্পর্ক রাখে যা আখিরাতের সাফল্যের উপযোগী হয়। দুনিয়ার সুযোগ-সুবিধা ও স্বার্থ লাভের জন্যে সকল প্রকার দ্বন্দ্বসংগ্রাম থেকে তারা দূরে থাকে। তারা সত্যনিষ্ঠ, সুবিচার, শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম গ্রহণ করে এবং এসবকেই গন্তব্যে পৌঁছার রাজপথ হিসেবে গ্রহণ করে।
ঠিক এর বিপরীত খোদা ও আখিরাতের প্রতি যাদের দৃঢ় প্রত্যয় নেই তাদের জীবনের সকল চেষ্টা-চরিত্রের লক্ষ্য হলো দুনিয়ার হীনস্বার্থ লাভ। ফলে পার্থিব স্বার্থ লাভের জন্যে সংঘাত-সংঘর্ষ ও যুদ্ধবিগ্রহ অনিবার্য হয়ে পড়ে। বর্তমান জগতে, যা প্রকৃতপক্ষে সেকিউলার জগত (SECULAR WORLD), মানুষে মানুষে, দেশে দেশে ও জাতিতে জাতিতে যুদ্ধ-বিগ্রহের বহ্নি প্রজ্জ্বলিত দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এ স্বার্থপরতা ও সুবিধাবাদ ছাড়া আর কিসের বহিপ্রকাশ? আজ সুযোগ-সুবিধা লাভেচ্ছু ও স্বার্থান্বেষী তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে অন্তহীন দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ মানবজাতিকে বার বার ভয়াবহ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের দিকে ঠেলে দিয়েছে ও দিচ্ছে। এ স্বার্থান্বেষী বুদ্ধিজীবীরা কারা? এরা ‘সেকিউলারিজমের’ই ধারক ও বাহক।
সুবিধাবাদ রাজনীতিকেও কলুষিত করছে এবং কোন কোন দেশে কল্যাণকর ও স্থিতিশীল কোন রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে জাতীয় সম্পদকে লুটেরাদের কুক্ষিগত করার সুযোগ করে দিচ্ছে। আইনের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা বিনষ্ট করছে এবং দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার পথ রুদ্ধ করা হচ্ছে। ক্ষমতাসীন দল অর্থ ও পদমর্যাদার বিনিময়ে রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীদের কেনাবেচার মাধ্যমে সুবিধাবাদকে জাতীয় জীবনে প্রতিষ্ঠিত করে জাতির চারিত্রিক মেরুদণ্ড ভেঙ্গে চুরমার করছে। ব্যক্তিস্বার্থ ও সুবিধাবাদ ‘সেকিউলারিজমের’ দু’টি অতি আকর্ষণীয় বস্তু- উন্নত মানবীয় চরিত্র ব্যতীত যার থেকে দূরে থাকা বড়ো কঠিন। এ দু’টিকে ‘অচ্ছুৎ’ বলে পরিহার করা তাদের পক্ষেই সম্ভব, যারা ইসলামের শিক্ষার ভিত্তিতে নিজেদের জীবন গড়ে তোলার চেষ্টা-সাধনা করে।
‘সেকিউলারিজমের’ চতুর্থ কুফল চরম নৈতিক অবক্ষয়। নৈতিক মূল্যবোধের ভিত মানুষের স্বভাব-প্রকৃতির মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে বিধায় তা জানা ও উপলব্ধি করা মোটেই কষ্টকর নয়। বরঞ্চ নৈতিক মূল্যবোধের বাস্তব অনুসরণ ও তার নির্দিষ্ট ছাঁচে জীবনকে ঢেলে সাজানো অবশ্যই কঠিন। এ মূল্যবোধ প্রতি পদে পদে কিছু বাধা-নিষেধ মানুষের কাছে দাবি করে। আর এ বাধা-নিষেধ অপেক্ষা কঠিন জিনিস মানুষের জন্যে আর কিছু নেই। এ মূল্যবোধের অনুসরণ অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে যখন মানুষের অতৃপ্ত লালসা-বাসনা ও প্রিয়বস্তুর সাথে তা সাংঘর্ষিক হয়ে পড়ে। নৈতিক মূল্যবোধের দাবিই তো এই যে, প্রবৃত্তির ওসব লালসা-বাসনা, হীনস্বার্থ ও পার্থিব সুযোগ-সুবিধা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করতে হবে। এজন্যে মানবজাতিকে নৈতিক দিক দিয়ে উন্নত করার জন্যে এতোটুকুই যথেষ্ট নয় যে, নৈতিক মূল্যবোধের কথা তাদের সামনে তুলে ধরতে হবে। বরঞ্চ সবচেয়ে বড়ো প্রয়োজন এমন এক শক্তিশালী প্রেরণাদায়ক কর্মপ্রক্রিয়ার যা নৈতিক বাধা-নিষেধ মেনে নেয়ার জন্যে মানুষের মনকে প্রস্তুত করতে পারে। সেকিউলারিজম এ প্রয়োজন পূরণ করেনি। বরঞ্চ সে প্রবৃত্তির কামনা-বাসনার দাবি হ্রাস করার পরিবর্তে বহুগুণে বাড়িয়ে দিয়ে মানুষকে তার দাস বানিয়ে দিয়েছে। সেকিউলারিজমের স্বাভাবিক ও অনিবার্য পরিণামস্বরূপ দায়িত্বানুভূতির শূন্যতা, প্রবৃত্তির দাসত্ব এবং স্বার্থসিদ্ধি ও সুযোগ-সুবিধা লাভের জন্যে সংঘাত-সংঘর্ষ মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অধঃপতন ডেকে এনেছে। নারী-পুরুষ ও শিশু নির্বিশেষে মানুষের উপর বর্ণনাতীত পৈশাচিক নির্যাতন, বছরের পর বছর এবং কারো কারো ক্ষেত্রে জীবনের অধিকাংশ সময় বিনা বিচারে কারাজীবন ভোগ, হত্যাযজ্ঞ ও নারী ধর্ষণ, সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদের মাধ্যমে দুর্বল দেশ ও জাতিকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দাসত্বের শৃঙ্খল পরিধান করতে বাধ্য করা প্রভৃতি অমানবিক ক্রিয়াকর্ম দেখে মনে হয় যেন মনুষ্যত্ব মৃত্যুবরণ করেছে এবং সমগ্র জগতে মানুষের আকৃতিতে হিংস্র পশুর রাজত্ব চলছে। সেকিউলারিজম চিন্তা-চেতনার ক্ষেত্রে, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে যে চরম অধঃপতন ডেকে এনেছে তারই কুফল মানবজাতিকে ভোগ করতে হচ্ছে। এর সমাধান একটিই এবং তা হচ্ছে এই যে, মন-মস্তিষ্ক ও জীবনের সকল ক্ষেত্র থেকে সেকিউলারিজম উৎখাত করে মানবজাতির জন্যে প্রদত্ত দয়াময় বিশ্বস্রষ্টার বিধান নতশিরে মেনে নেয়া এবং আখিরাতে জবাবদিহির তীব্র অনুভূতির ভিত্তিতে গোটা জীবনকে গড়ে তোলা। আর এ জীবন গড়ার বুনিয়াদ বানাতে হবে জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থাকে।
জাতীয়তাবাদ
জাহেলিয়াতের প্রথম অস্ত্র ‘সেকিউলারিজম’-এর আলোচনার পর দ্বিতীয় অস্ত্র জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে আলোচনা করে দেখা যাক যে, গোটা মানবজাতির জন্যে এ কতটা মারাত্মক।
খৃস্টীয় পোপ ও রোমান সম্রাটদের বিশ্বব্যাপী স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে যে প্রতিক্রিয়ার বিস্ফোরণ ঘটে, তার থেকে জাতীয়তাবাদ তথা জাতিপূজার সূচনা হয়। সূচনাকালে এর অর্থ শুধু এতোটুকু ছিল যে, বিভিন্ন জাতি তাদের নিজেদের রাজনীতি ও বিচার-বিবেচনার নিরংকুশ অধিকারী হবে। তারা কোন বিশ্বজনীন আধ্যাত্মিক অথবা রাজনৈতিক শক্তির দাবার গুটি হিসেবে ব্যবহৃত হবে না। কিন্তু এ নিষ্পাপ সূচনা থেকে এ চিন্তা-চেতনা যখন সম্মুখে অগ্রসর হলো, তখন এ এমন স্থানে গিয়ে উপনীত হলো যে, যে স্থানে থেকে ধর্মহীনতা তথা সেকিউলারিজমের আন্দোলন খোদাকে অপসারিত করেছিল, সেখানে জাতীয়তাবাদকে অধিষ্ঠিত করে দিল। ক্রমশঃ এখন প্রত্যেক জাতির মহানতম নৈতিক মূল্যবোধ হয়ে পড়েছে তার জাতীয় স্বার্থ, জাতীয় আশা-আকাংক্ষা ও উচ্চাভিলাষ। এখন পুণ্য কাজ তা-ই হয়ে পড়েছে যা জাতির জন্যে কল্যাণকর তা সে মিথ্যা হোক, বিশ্বাসঘাতকতা হোক, জুলুম-অত্যাচার হোক অথবা অন্য কোন কর্মকাণ্ড হোক, যা প্রাচীন ধর্ম ও নৈতিকতার দৃষ্টিতে যতো বড়ো পাপই মনে করা হোক না কেন। আর পাপ কাজ তা-ই মনে করা হয়, যা জাতীয় স্বার্থের জন্যে ক্ষতিকর, তা সত্যবাদিতা হোক, সুবিচার হোক, অধিকার পূরণ করা হোক অথবা এমন কোন কাজ হোক যা এককালে চারিত্রিক মাধুর্য বলে গণ্য করা হতো। জাতির ব্যক্তিবর্গের গুণাবলী, জীবন ও কর্মতৎপরতার মাপকাঠি এই যে, জাতীয় স্বার্থ তাদের নিকটে যে ত্যাগ ও কুরবানী দাবি করবে, তা জান ও মালের কুরবানী হোক অথবা নৈতিকতা, মনুষ্যত্ব ও আত্মসম্ভ্রমের কুরবানী হোক, তার জন্যে তারা কোন দ্বিধাবোধ করবে না এবং ঐক্যবদ্ধ হয়ে জাতির ক্রমবর্ধমান উচ্চাভিলাষ পূরণে বদ্ধপরিকর থাকবে। সামগ্রিক চেষ্টা চরিত্রের লক্ষ্য এখন এই যে, প্রত্যেক জাতি তার ব্যক্তিবর্গের মধ্যে ঐক্য-শৃংখলা সৃষ্টি করবে যাতে অন্যান্য জাতির মুকাবিলায় স্বীয় জাতীয় পতাকা সমুন্নত করতে পারে।
অবশ্যি জাতীয়তার (NATIONALITY) বিরুদ্ধে কারো কোন আপত্তি থাকার কথা নয়। কারণ এ এক স্বাভাবিক বাস্তবতা। অতএব জাতির শুভাকাঙ্ক্ষার বিরোধিতা করা যায় না, যদি তার মধ্যে অন্য জাতির প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রুতার মনোভাব না থাকে। জাতির জন্যে প্রেম ও ভালোবাসা কখনো নিন্দনীয় হতে পারে না, অবশ্য যদি এ প্রেম ও ভালোবাসা আপন জাতির জন্যে অন্যায় পক্ষপাতিত্ব এবং অন্যান্য জাতির জন্যে হিংসা ও শত্রুতার কারণ না হয়। প্রত্যেক জাতির স্বাধীনতাকেও অবশ্যই সমর্থন করতে হবে। কারণ নিজেদের ব্যাপার ও বিষয়াদি নিজের দ্বারাই মীমাংসিত হওয়া ও আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা নিজেই সম্পন্ন করা প্রত্যেক জাতির অধিকার এবং কোন জাতির উপর অন্য কোন জাতির আধিপত্য কিছুতেই ন্যায়সঙ্গত হতে পারে না। যা অন্যায় ও পরিহারযোগ্য তা হচ্ছে জাতীয়তাবাদ (NATIONALISM) বা জাতিপূজা। জাতীয় অন্ধ স্বার্থপরতার দ্বিতীয় নামই জাতীয়তাবাদ। এর মূলনীতি এই যে, সত্য ও সঠিক তা-ই যা জাতীয় স্বার্থের অনুকূল এবং মিথ্যা ও অন্যায় তা-ই যা অনুকূল নয়। জাতীয় স্বার্থের অন্ধ আবেগে অন্য জাতির রক্ত পান করা, অন্য দেশ জবরদখল করা, অন্য দেশ ও জাতির ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করা, বিজিত দেশের সকল সম্পদ ও নারী উপভোগের উপর অবাধ অধিকার প্রতিষ্ঠিত করা কোন অন্যায় নয়, বরঞ্চ জাতীয় গৌরব মনে করা হয়। অপরের তুলনায় আপন জাতিকে শ্রেষ্ঠতর ও অধিক শক্তিশালী প্রমাণ করার জন্যে ভূখণ্ডের পর ভূখণ্ড জয় করা জাতীয়তাবাদেরই দাবি। তাই দুনিয়ায় মানবজাতির জন্যে জাতীয়তাবাদকে বিরাট অভিশাপ মনে করা হয়েছে। যদি একটি সমাজের মধ্যে সে ব্যক্তির অস্তিত্ব একটি অভিশাপ হয় যে তার প্রবৃত্তি ও স্বার্থের দাস হয়ে পড়েছে এবং আপন স্বার্থের জন্যে সবকিছু করতে প্রস্তুত; যদি একটি জনপদের মধ্যে সেই পরিবারটি একটি অভিশাপ হয় যার লোকজন পারিবারিক স্বার্থের অন্ধ পূজারী হয়ে পড়ে এবং ন্যায় অন্যায় যে কোন উপায়ে পরিবারের স্বার্থ হাসিলের জন্য বদ্ধপরিকর; যদি একটি দেশের মধ্যে সেই শ্রেণীটি একটি অভিশাপ হয় যে শ্রেণীস্বার্থের অন্ধ পূজারী হয় এবং অন্যের ভালো-মন্দের তোয়াক্কা না করে আপন স্বার্থ উদ্ধারের পেছনেই লেগে থাকে, যেমন চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, কালোবাজারি, চোরাচালানি প্রভৃতি সমাজবিরোধী কাজে লিপ্ত থাকে, তাহলে বিরাট ও বিশাল পরিমণ্ডলে সে স্বার্থান্ধ জাতি কেন একটি অভিশাপ হবে না যার আচরণ উপরে বর্ণনা করা হলো? এ অন্ধ জাতিপূজার আবেগ-অনুরাগ দু’টি বিশ্বযুদ্ধসহ বহু ছোট-বড়ো যুদ্ধের অনল প্রজ্জ্বলিত করে কত জাতি ও দেশ ছারখার করেছে, কত লক্ষ লক্ষ মানবসন্তানকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছে, কত লক্ষ লক্ষ মানুষকে পঙ্গু ও বিকলাঙ্গ করেছে।
জাতীয়তাবাদ নয়, বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বই মানবজাতিকে ধ্বংস থেকে রক্ষা করতে পারতো, আর এ বিশ্বভ্রাতৃত্বের উদার আহ্বান জানিয়েছিল ইসলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, এ ইসলামের বাণীবাহক ছিল যে মুসলিম জাতি, সে আজ জাতীয়তাবাদকে খোদার আসনে অধিষ্ঠিত করেছে। আজ সমগ্র দুনিয়ায় এ জাতীয়তাবাদ; ভৌগোলিক জাতীয়তাবাদ, ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদ অথবা বংশ, গোত্র ও বর্ণভিত্তিক জাতীয়তাবাদ- মানবজাতির জন্যে এক বিরাট অভিশাপ হয়ে পড়েছে। জাতীয়তাবাদ তথা জাতিপূজার নীতি এই যে, সত্য ও সঠিক তা-ই যা জাতীয় স্বার্থের উপযোগী এবং মিথ্যা ও অন্যায় তা-ই যা জাতীয় স্বার্থের উপযোগী নয়। প্রত্যেকের বিবেক অবশ্যই সাক্ষ্য দেবে যে, সকল স্বার্থবাদিতা ও আত্মপূজার ন্যায় এ জাতীয় স্বার্থপরতা ও জাতীয় পূজাও এক বিরাট অভিশাপ। এ অভিশাপে আজ গোটা বিশ্ব জর্জরিত।
পরম পরিতাপের বিষয় এই যে, যে মুসলমানদের মধ্যে আল্লাহর কালামে পাক এবং রসূলের (সা) সুন্নাহ বিদ্যমান রয়েছে একেবারে অবিকৃত অবস্থায়, রয়েছে বিশ্বভ্রাতৃত্বের ইসলামী পয়গাম, সে মুসলমান আজ ভৌগোলিক ও ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদের অভিশাপে জর্জরিত এবং এটাই জাহেলিয়াতের বিজয় বা কৃতিত্ব।
প্রাচীন জাহেলিয়াতের যুগে বংশে বংশে, গোত্রে গোত্রে, অঞ্চলে অঞ্চলে যে পারস্পরিক শত্রুতা ও দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ চলে আসছিল যুগের পর যুগ ও শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে, ইসলাম এসে তার অবসান ঘটিয়ে সবাইকে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে একত্র করে দিল, ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে সকল দল ও গোষ্ঠীকে এক ও অভিন্ন করে দিল। এ ইসলামী জাতীয়তা ও বিশ্বভ্রাতৃত্ব মুসলমানদের এক গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস তৈরি করেছিল, প্রায় অর্ধ পৃথিবীর উপরে ইসলামের বিজয় পতাকা উড্ডীন করেছিল। অতঃপর জাহেলিয়াত তাদেরকে জাতিপূজায় উদ্বুদ্ধ করলো। মুসলমানের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য আল্লাহতায়ালার সন্তুষ্টি লাভ এবং এর জন্যেই তাদের সকল চেষ্টা-চরিত্র, সাধনা ও জানমালের কুরবানী। এখন তাদের সকল চেষ্টা-চরিত্র ও সাধনা হয়ে পড়েছে জাতি-খোদার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যে। এ সন্তুষ্টি অর্জন করতে গিয়ে অন্য জাতির প্রতি কোন অন্যায়, এমনকি কোন ভ্রাতৃপ্রতিম মুসলিম দেশের বিরুদ্ধে আগ্রাসন করা হোক না কেন, সেটাকে দূষণীয় মনে করা হয় না কিছুতেই। জাতির স্বার্থ হাসিলের জন্যে যে কোন দেশ, (তা মুসলিম হোক, অমুসলিম হোক) জবরদখল করাকে নেক কাজ মনে করা হয়। যারা খোদা ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাসী নয়, তারা জাতীয়তাবাদের মন্ত্রে দীক্ষিত হতে পারে, জাতীয় স্বার্থের জন্যে অন্য জাতির জান-মাল-ইজ্জত আব্রু লুণ্ঠন করতে পারে এবং তাদের এ জাতীয় উচ্চাভিলাষ ও লালসা-বাসনা দু’টি বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত করেছে। কোন উচ্চতম শক্তিমান সত্তার নিকটে জবাবদিহির অনুভূতি তাদের নেই বলে জাতীয় স্বার্থকেই তারা জীবনের লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করেছে। কিন্তু এ পথে মুসলমানদেরকে টেনে নিয়ে আসা আলবৎ জাহেলিয়াতের কৃতিত্বই বলতে হবে।
গণতন্ত্র
জাহেলিয়াতের তৃতীয় মারাত্মক অস্ত্র গণতন্ত্র তথা জনগণের সার্বভৌমত্ব। নিরংকুশ শাসন ক্ষমতার অধিকারী রাজা-বাদশাহ ও অন্যান্য স্বৈরাচারী শাসকদের একচ্ছত্র আধিপত্য খতম করার জন্যে গণতন্ত্রের ধারণা পেশ করা হয়। অর্থাৎ জনসাধারণের সুযোগ-সুবিধা ও অভাব-অভিযোগের প্রতি লক্ষ্য রেখে জনসাধারণের মতামতের ভিত্তিতেই শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হবে। এ ধারণা অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত যে, লক্ষ-কোটি মানুষের উপর এক ব্যক্তি, পরিবার অথবা গোষ্ঠীর খেয়াল-খুশি ও মর্জি চাপিয়ে দেয়ার এবং আপন স্বার্থ ও মর্জি পূরণের জন্যে তাদেরকে ব্যবহার করার কোনই অধিকার থাকতে পারে না। কিন্তু এ নেতিবাচক দিকটির সাথে যে ইতিবাচক দিকটি ছিল তা এই যে, এক এক দেশ ও এক এক অঞ্চলের অধিবাসী নিজেরাই শাসক ও নিজেরাই মালিক। এ ইতিবাচক দিকটির উপর গণতন্ত্র সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার পর যে আকার ধারণ করে তা এই যে, প্রত্যেক জাতি তার ইচ্ছা ও মর্জি পূরণের নিরংকুশ অধিকারী। তার সামগ্রিক ইচ্ছা-বাসনা অথবা তার সংখ্যাগরিষ্ঠের ইচ্ছা-বাসনা দমিত করার শক্তি আর কারো নেই। নীতি-নৈতিকতা হোক, সভ্যতা-সংস্কৃতি হোক, সামাজিকতা হোক অথবা রাজনীতি হোক, প্রতিটি ক্ষেত্রে সঠিক নীতি তা-ই হবে যা জাতীয় অভিলাষের ভিত্তিতে নির্ণীত হবে। যে নীতি জনমত প্রত্যাখ্যান করবে তা ভ্রান্ত ও অন্যায়। আইন জাতির ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। ইচ্ছা করলে যে কোন আইন প্রণয়ন করবে এবং ইচ্ছা করলে যে কোন আইন রহিত করবে। জাতির মর্জি অনুযায়ী সরকার গঠিত হবে এবং সরকার জাতির মর্জি পূরণে বাধ্য থাকবে। সরকার তার সকল শক্তি নিয়োজিত করবে জাতির মর্জি পূরণের জন্যে।
জাহেলিয়াতের আবিষ্কৃত উপরে উল্লেখিত তিনটি মতবাদ সেকিউলারিজম তথা ধর্মহীনতা বা খোদাদ্রোহীতা, জাতীয়তাবাদ এবং গণতন্ত্র জীবনের সকল বিভাগ, সমাজ ও রাষ্ট্রের সকল ক্ষেত্র থেকে খোদার প্রভুত্ব-কর্তৃত্ব ও আনুগত্য প্রত্যাখ্যান করেছে। জাতি ও জনসাধারণকে খোদার আসনে অধিষ্ঠিত করেছে।
ইসলামের সুস্পষ্ট ঘোষণা এই যে, সার্বভৌমত্বের অধিকারী একমাত্র আল্লাহ (SOVEREIGNTY BELONGS TO ALLAH ALONE)। আর এটা ইসলামী ঈমান-আকীদার কথা। আসমান যমীন এবং মানুষসহ প্রতিটি জীব ও জন্তুর স্রষ্টা একমাত্র আল্লাহ। তিনি সকলের প্রভু ও প্রতিপালক। তিনি মানবজাতির বাদশাহও। মানুষ তাঁর প্রজা। সৃষ্টি ও প্রজার উপরে স্রষ্টা ও বাদশাহেরই আইন-শাসন ও প্রভুত্ব চলবে- এটাই অত্যন্ত স্বাভাবিক ও ন্যায়সংগত কথা। আইন-শাসনের এ স্বাভাবিক ও ন্যায়সঙ্গত অধিকার- যাকে সার্বভৌমত্ব বলা হয়, আল্লাহর নিকট থেকে কেড়ে নিয়ে দেয়া হচ্ছে জনসাধারণকে। গণতন্ত্রের প্রথম ও মূলকথা হচ্ছে – SOVEREIGNTY BELONGS TO THE PEOPLE- সার্বভৌমত্ব জনগণের। তারা যেভাবে খুশি দেশ ও জাতির জন্যে আইন প্রণয়ন করবে এবং যখন খুশি যে কোন আইন রহিত করবে। জনগণকে আইন রচনার অধিকার দেয়ার ফলে দেখা যায়- একই বস্তু কখনো বৈধ, আবার কখনো অবৈধ ঘোষণা করা হয়। আমেরিকায় একবার মদ্যপানের সর্বনাশা পরিণাম লক্ষ্য করে, তা আইন করে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। কিন্তু যে জনসাধারণ আইন রচনার অধিকারী, সে জনগণের চাপেই আবার মদ্যপান বৈধ ঘোষিত হয়। গর্ভপাত বা ভ্রূণহত্যা সকল ধর্মে নিষিদ্ধ এবং বিবেকও তা-ই বলে। কিন্তু চরম নৈতিক অবক্ষয় ও যৌন অনাচারের ফলে যখন জনমত গর্ভপাতের দাবি জানায়, তখন আইন করে তা বৈধ ঘোষণা করা হয়। অত্যন্ত ঘৃণিত ও লজ্জাকর কাজ সমকামিতা (HOMO SEXUALITY)। জনগণের মধ্যে যখন সমকামিতার ব্যাধি মহামারীর আকারে ছড়িয়ে পড়লো, তখন আইন করে এ অত্যন্ত গর্হিত পাপকাজ বৈধ বলে ঘোষণা করা হলো। যে মানুষ কখনো ভুল-ত্রুটির ঊর্ধ্বে হতে পারে না এবং যার জ্ঞান অত্যন্ত সীমিত তাকে আইন রচনার পূর্ণ স্বাধীনতা দিলে মানব সমাজ বিশৃঙ্খলা, অবিচার ও পাপাচারেই পূর্ণ হতে পারে।
প্রকৃত ব্যাপার এই যে, কোনটি ভালো এবং কোনটি মন্দ, কোনটি কল্যাণকর ও কোনটি অকল্যাণকর তার পরিপূর্ণ জ্ঞান একমাত্র আল্লাহতায়ালারই রয়েছে। তাই তিনি মানুষের জন্যে যা ভালো ও মন্দ, হালাল ও হারাম নির্ধারিত করে দিয়েছেন- যে আইন অথবা আইনের মূলনীতি ঘোষণা করেছেন- তা অভ্রান্ত এবং মানুষের জন্যে একমাত্র কল্যাণকর। যিনি বিশ্ব প্রকৃতির স্রষ্টা ও ব্যবস্থাপক তিনি সকল ভুলের ঊর্ধ্বে। অতএব তাঁর আইনও নির্ভুল হতে বাধ্য। তাঁর আইন অথবা কোন বিষয়ের ফয়সালা পরিবর্তনের অধিকার কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী অথবা কোন দেশের পার্লামেন্টের নেই। তা কেউ করলে তা একদিকে যেমন খোদাদ্রোহিতা হবে অপরদিকে তা মানুষের অকল্যাণই ডেকে আনবে।
“আল্লাহ বলেন, কোন মুমিন পুরুষ অথবা মুমিনা নারীর এ অধিকার নেই যে, আল্লাহ ও তাঁর রসূল কোন বিষয়ে ফয়সালা করে দিয়ে থাকলে সে ব্যাপারে সে নিজে কোন ফয়সালা করার এখতিয়ার রাখবে”- (সূরা আল আহযাবঃ ৩৬)।
সমগ্র প্রকৃতি ও মানুষের স্রষ্টা, প্রভু ও বাদশাহ হিসেবে মানুষের জন্যে সুষ্ঠু কল্যাণকর আইন একমাত্র আল্লাহতায়ালাই রচনা করতে পারেন এবং তাঁর নির্দেশে তাঁর রসূলও আইন রচনা করতে পারতেন। কিন্তু জাহেলিয়াত এ আইন রচনার অধিকার নিরংকুশভাবে জনসাধারণকে তথা জনপ্রতিনিধিদের হাতে অর্পণ করেছে। এ ইসলামী আকীদাহ-বিশ্বাসের পরিপন্থী, বিবেকের এবং মানব কল্যাণের পরিপন্থী।
উপরে জাহেলিয়াতের মারাত্মক যে তিনটি মতবাদ বা মূলনীতির আলোচনা করা হলো, তার জবাবে ইসলাম অন্য তিনটি মূলনীতি পেশ করেছে। মানুষের বিবেকের কাছে আমরা অবশ্যই আবেদন জানাব এ তিনটি যাচাই ও পরীক্ষা করে দেখার জন্যে যে, মানবকল্যাণ প্রকৃতপক্ষে কোন তিনটির মধ্যে নিহিত। ইসলামের সে তিনটি মূলনীতি হচ্ছেঃ
১। সেকিউলারিজম তথা ধর্মহীনতার মুকাবিলায় জীবনের সকল ক্ষেত্রে খোদার দাসত্ব-আনুগত্য।
২। জাতিপূজার মুকাবিলায় মানবতা।
৩। জনগণের সার্বভৌমত্বের মুকাবিলায় খোদার সার্বভৌমত্ব ও জনগণের খিলাফত।
প্রথম মূলনীতির মর্ম এই যে, আমরা সকলে সেই খোদাকে আমাদের প্রভু বলে মেনে নেব, যিনি আমাদের এবং সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতির স্রষ্টা, মালিক ও শাসক। আমরা তাঁর থেকে স্বাধীন ও বেপরোয়া হয়ে নয়, বরঞ্চ তাঁর অনুগত হয়ে এবং তাঁর পথনির্দেশনা মেনে নিয়েই জীবন যাপন করব। আমরা শুধু তাঁর পূজা-অর্চনাই করব না, বরঞ্চ তাঁর আনুগত্য এবং দাসত্বও করব। আমরা শুধু আমাদের ব্যক্তি জীবনেই তাঁর হুকুম ও হেদায়েত মেনে চলব না, বরঞ্চ আমাদের সামষ্টিক-সামাজিক জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্র ও বিভাগে তাঁরই অনুগত হয়ে থাকব। আমাদের সমাজ, সভ্যতা-সংস্কৃতি, রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষাব্যবস্থা, আমাদের শাসন ও বিচার ব্যবস্থা, আমাদের যুদ্ধ ও সন্ধি, আমাদের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক-সম্বন্ধ- মোটকথা সবকিছুই সেই মূলনীতি ও সীমারেখার মধ্যেই হবে যা খোদা নির্ধারিত করে দিয়েছেন। পার্থিব বিষয়াদি নির্ণয় করার ব্যাপারে আমরা একেবারে স্বাধীন হবো না, বরঞ্চ আমাদের স্বাধীনতা সে সীমারেখার মধ্যেই সীমিত থাকবে, যা খোদার নির্ধারিত মূলনীতি টেনে দিয়েছে। এ মূলনীতি এবং সীমারেখা সর্বাবস্থায় আমাদের এখতিয়ার বহির্ভূত।
দ্বিতীয় মূলনীতির মর্ম এই যে, খোদাপরস্তির ভিত্তিতে যে জীবনব্যবস্থা গড়ে উঠে, সেখানে জাতি, বংশ, জন্মভূমি, বর্ণ ও ভাষার পার্থক্যের ভিত্তিতে কোন প্রকার পক্ষপাতিত্ব ও স্বার্থপরতার কোন স্থান থাকবে না। তা একটি জাতীয় ব্যবস্থার পরিবর্তে একটি নীতিগত ব্যবস্থা হওয়াই বাঞ্ছনীয়- যার দ্বার উন্মুক্ত থাকবে প্রত্যেক সে মানুষের জন্যে যে তার মূলনীতি মেনে নেবে। আর যে ব্যক্তিই তা মেনে নেবে সে কোনরূপ বৈষম্য ব্যতিরেকেই সমঅধিকারের ভিত্তিতে তাতে শরীক হতে পারবে। এ ব্যবস্থার অধীনে নাগরিকত্ব (CITIZENSHIP) নিছক একটি রাষ্ট্রের ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যেই সীমিত হবে না, বরঞ্চ মূলনীতির ভিত্তিতে সার্বজনীন হবে। যারা এ মূলনীতির সাথে একমত নয় অথবা কোন কারণে তা মেনে নিতে রাজি নয়, তাদেরকে দমিত করা ও নির্মূল করা যাবে না। বরঞ্চ তারা নির্দিষ্ট অধিকারসহ এ ব্যবস্থার অধীনে নিরাপদে থাকবে এবং তাদের জন্যে সর্বদা এ সুযোগ থাকবে যে, যখনই এসব মূলনীতির সত্যতা স্বীকার করে নিয়ে নিশ্চিন্ত হবে, তখনই তারা সমঅধিকারসহ নিজেদের স্বাধীন মর্জিমতো এ ব্যবস্থায় কর্তৃত্বশীল হতে পারবে।
এ বস্তুকে আমরা মানবতার নীতি বলে আখ্যায়িত করছি এবং তা জাতীয়তার পরিপন্থী নয়। বরঞ্চ তাকে তার প্রকৃত স্বাভাবিক সীমার মধ্যে রাখতে চাই। এতে জাতীয় প্রেমের স্থান আছে, কিন্তু জাতীয় পক্ষপাতিত্বের স্থান নেই। জাতির জন্যে শুভাকাঙ্ক্ষাও জায়েজ, কিন্তু জাতীয় স্বার্থপরতা হারাম। জাতীয় স্বাধীনতা সর্বস্বীকৃত এবং একটি জাতির উপর অন্য জাতির আধিপত্যও মেনে নেয়া যায় না- যা মানবতাকে অনতিক্রমণীয় সীমারেখার মধ্যে বিভক্ত করে দেয়। মানবতার নীতির দাবি এই যে, যদিও প্রত্যেক জাতি তার আভ্যন্তরীণ বিষয়াদির ব্যবস্থাপনা নিজেই করবে, এবং কোন জাতি জাতি হিসেবে অন্য কোন জাতির অধীন হবে না, কিন্তু যেসব জাতি মানবসভ্যতার বুনিয়াদী মূলনীতির সাথে একমত, তাদের মধ্যে মানবতার কল্যাণ ও উন্নতির কাজে পূর্ণ সহযোগিতা থাকবে। প্রতিযোগিতার (COMPETETION) পরিবর্তে সহযোগিতা হবে। পারস্পরিক পার্থক্য, বিদ্বেষ ও ভিন্নতা থাকবে না। সভ্যতা-সংস্কৃতি ও জীবনের উপায়-উপকরণের স্বাধীনভাবে লেনদেন হবে। আর এ সভ্য জীবনব্যবস্থার অধীনে বসবাসকারী দুনিয়ার প্রতিটি মানুষ এক জাতি ও এক দেশের নয়, বরঞ্চ এ সমগ্র দুনিয়ার নাগরিক হবে, যেন সে একথা বলতে পারেঃ যেহেতু সকল দেশ আমার খোদার, সেহেতু প্রত্যেক দেশও আমার। বর্তমানে এমন এক অবাঞ্ছিত অবস্থা বিরাজ করছে যে, এক ব্যক্তি না স্বয়ং আপন জাতি ও দেশ ব্যতীত অন্য কোন জাতি ও দেশের বিশ্বস্ত হতে পারে। আর না কোন জাতি তার আপন লোক ব্যতীত অন্য কোন জাতির লোকের প্রতি আস্থা রাখতে পারে। মানুষ তার দেশের সীমান্ত অতিক্রম করার সাথে সাথেই অনুভব করে যে, খোদার দুনিয়ার প্রতিটি স্থানে তার জন্যে শুধু প্রতিবন্ধকতাই রয়েছে। প্রত্যেক স্থানে তাকে যেন চোর-ডাকাতের মতো সন্দেহের চোখে দেখা হয়। প্রত্যেক স্থানে জিজ্ঞাসাবাদ ও তল্লাশি। কথাবার্তা ও চলাফেরায় বাধানিষেধ। কোথাও তার জন্যে না স্বাধীনতা আছে না অধিকার। তার মুকাবিলায় আমরা এমন এক বিশ্বজনীন ব্যবস্থা দেখতে চাই যেখানে মূলনীতির ঐক্যের ভিত্তিতে জাতিগুলোর মধ্যে ফেডারেশন হবে এবং এ ফেডারেশনের মধ্যে সমান ও সার্বজনীন নাগরিকত্ব (COMMON CITIZENSHIP) ও অবাধ যাতায়াত ব্যবস্থা প্রচলিত হবে। আমাদের চোখ যেন আর একবার এ দৃশ্য দেখতে পারে যে, আজকালের কোন ‘ইবনে বতুতা’ আটলান্টিক উপকূল থেকে কৃষ্ণ সাগরের উপকূল পর্যন্ত এমনভাবে ভ্রমণ করবেন যে, কোথাও তিনি বিদেশী (FOREIGNER) বলে গণ্য হবেন না।
এখন তৃতীয় মূলনীতির কথাই ধরা যাক। আমরা জনগণের সার্বভৌমত্ব বা বাদশাহীর (SOVEREIGNTY) পরিবর্তে জনগণের খিলাফত চাই। ব্যক্তি রাজতন্ত্র বা বাদশাহী (MONARCHY), আমীর-ওমরার শাসনক্ষমতা এবং শ্রেণীসমূহের একচেটিয়া অধিকারের আমরা ততোটা বিরোধী, যতোটা আধুনিককালের একজন চরম গণতন্ত্রী হয়ে থাকেন। পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের অতি উৎসাহী সমর্থকদের ন্যায় আমরাও সামাজিক জীবনে সকলের সমান অধিকার ও সুযোগ-সুবিধার দাবি করি। আমাদেরও একথা যে, শাসন পরিচালনার ব্যবস্থাপনা এবং শাসকদের নির্বাচন জনগণের স্বাধীন মতামতের ভিত্তিতে হতে হবে। সেইসাথে আমরা এমন জীবনব্যবস্থার চরম বিরোধী যেখানে সভা-সমিতির স্বাধীনতা এবং কোন আন্দোলন ও সংগ্রাম করার স্বাধীনতা নেই। অথবা যেখানে জন্ম, বংশ ও শ্রেণীর কিছুলোকের জন্যে বিশেষ অধিকার সংরক্ষিত থাকবে এবং অন্যদের জন্যে থাকবে বিশেষ প্রতিবন্ধকতা। এই হচ্ছে গণতন্ত্রের মূল সারাংশ যে ব্যাপারে আমাদের গণতন্ত্র এবং পাশ্চাত্যের গণতন্ত্রের মধ্যে কোন মতপার্থক্য নেই। এর মধ্যে এমন একটিও নেই যা পাশ্চাত্য আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছে। এ গণতন্ত্রের সাথে আমরা সে সময় থেকেই পরিচিত ছিলাম এবং দুনিয়ার সামনে এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্তও তুলে ধরেছিলাম, যার বহু শতাব্দী পর পাশ্চাত্যের আধুনিক গণতন্ত্রের সূচনা হয়। প্রকৃতপক্ষে এ নবজাত গণতন্ত্রের যে বিষয়টির সাথে আমাদের মতপার্থক্য তা হচ্ছে এই যে, এতে জনগণের নিরংকুশ সার্বভৌমত্ব বা বাদশাহীর নীতি পেশ করা হয়েছে যা বাস্তবতার দিক দিয়ে ভ্রান্ত এবং পরিণামের দিক দিয়ে অত্যন্ত মারাত্মক। প্রকৃতপক্ষে বাদশাহীর (SOVEREIGNTY) অধিকার একমাত্র তাঁর যিনি মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন, তাদের প্রতিপালন ও পরিবর্ধনের উপায় উপকরণ সরবরাহ করছেন, যাঁর ইচ্ছায় মানবজাতির ও সমগ্র সৃষ্টিজগতের অস্তিত্ব বিদ্যমান এবং যাঁর শক্তিশালী আইনের বন্ধনে সৃষ্টি জগতের প্রতিটি বস্তু আবদ্ধ। তাঁর বাস্তব ও প্রকৃত বাদশাহীর অধীনে যে বাদশাহীরই দাবি করা হোক না কেন তা এক ব্যক্তি অথবা পরিবারের বাদশাহী হোক, অথবা একটি জাতি ও তার জনগণের হোক সর্বাবস্থায় তা একটি বিভ্রান্তি ব্যতীত কিছু নয়। এ বিভ্রান্তির আঘাত প্রকৃত বাদশাহের গায়ে লাগবে না, বরঞ্চ লাগবে সে নির্বোধ বাদশাহীর দাবিদারের উপর যে তার আপন মর্যাদা সম্পর্কে অপরিজ্ঞাত। এ সত্যের আলোকে এটাই সঠিক যে, খোদাকে খোদা মেনে নিয়ে, মানবজীবনের শাসনব্যবস্থা খিলাফতের ধারণা-মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এ খিলাফত নিঃসন্দেহে গণতান্ত্রিক হতে হবে। স্বাধীন জনমতের ভিত্তিতেই সরকারপ্রধানের নির্বাচন হতে হবে। জনগণের মতামতের ভিত্তিতেই পার্লামেন্ট (শুরা) সদস্য নির্বাচিত হবেন। তাদের পরামর্শক্রমেই সরকারের যাবতীয় ব্যবস্থাপনা চলতে থাকবে। সরকারের সমালোচনা ও জিজ্ঞাসাবাদের তাদের পূর্ণ অধিকার থাকবে। কিন্তু এ সবকিছু এ অনুভূতিসহ হতে হবে যে, দেশ খোদার। আমরা মালিক নই, বরঞ্চ তাঁর প্রতিনিধি। আমাদের প্রতিটি কাজের হিসাব প্রকৃত মালিকের নিকট দিতে হবে। আল্লাহতায়ালা আমাদের জীবনের জন্যে যেসব চারিত্রিক মূলনীতি, আইনগত নির্দেশ ও সীমারেখা নির্ধারিত করে দিয়েছেন, তা যথাযথ আপন আপন স্থানে বলবৎ ও অটল থাকবে। আমাদের পার্লামেন্টের বুনিয়াদী দৃষ্টিভঙ্গি এ হতে হবে যে, আল্লাহর কুরআন এবং তাঁর রসূলের (সা) সুন্নাহ হবে সকল আইনের উৎস। আল্লাহ ও তাঁর রসূল যেসব বিষয়ে হেদায়েত ও আইনগত নির্দেশ দিয়েছেন সেসব বিষয়ে নতুন কোন আইন প্রণয়ন না করে তাঁদের নির্দেশ কার্যকর করার জন্যে বিস্তারিত কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। যেসব ব্যাপারে তাদের কোন হেদায়েত নেই, আমাদের মনে করতে হবে যে, সেসব ব্যাপারে আমাদেরকে কর্ম স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। অতএব শুধুমাত্র এসব ব্যাপারে আমরা পরামর্শের ভিত্তিতে আইন রচনা করতে পারব। কিন্তু এসব আইন অবশ্যই সেই সামগ্রিক কাঠামোর মেজাজ প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যশীল হতে হবে যা খোদার মৌলিক হেদায়েত আমাদের জন্যে তৈরি করে দিয়েছে।
অতঃপর যে জিনিসের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন তা হলো এই যে, এ গোটা রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব এমন সব লোকের উপর অর্পণ করা হবে যারা সর্বদা খোদার ভয়ে ভীত থাকে। তাঁর আনুগত্য করে এবং তারা তাদের প্রত্যেকটি কাজে খোদার সন্তুষ্টি লাভের অভিলাষী। তাদের জীবন এ সাক্ষ্যই দেয় যে, খোদার সামনে হাজির হয়ে জবাবদিহি করার প্রতি তাদের দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে।
উপরের পৃষ্ঠাগুলোতে জাহেলিয়াতের তিনটি মারাত্মক মতবাদ ও দর্শনের আলোচনা করা হলো এবং সেইসাথে ইসলামী আকীদাহ-বিশ্বাস, মতবাদ ও দৃষ্টিভঙ্গিও পেশ করা হলো। প্রত্যেক বিবেকবান ব্যক্তির নিকট জিজ্ঞাস্য যে, জাহেলিয়াতের এ তিনটি মতবাদের ভিত্তিতে সমগ্র দুনিয়ার প্রায় সকল দেশে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সভ্যতা-সংস্কৃতির যে প্রাসাদ গড়ে উঠেছে, তা কি মানুষের জীবনে কোন সুখ-শান্তি, জান-মালের নিরাপত্তা, সুবিচার, শান্তি-শৃংখলা প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে? মানুষে মানুষে, জাতিতে জাতিতে যুদ্ধ-বিগ্রহাদি, জানমালের অপূরণীয় ক্ষয়ক্ষতি, দুর্ভিক্ষ, অনাহার-দারিদ্র্য, মহামারী, দুরারোগ্য যৌনব্যাধি, চরম নৈতিক অবক্ষয়, হিংসা-বিদ্বেষ, হিংস্রতা-পরশ্রীকাতরতা প্রভৃতি যা মানবসমাজে অশান্তির মূল কারণ- তা কি বন্ধ হয়েছে, না হওয়ার কোন সম্ভাবনা আছে? যদি না হয়ে থাকে, তাহলে এখন সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় এসেছে যে, আমরা কি জাহেলিয়াতের মতবাদকে আঁকড়ে ধরে থেকে আমাদের ধ্বংস টেনে আনব, না বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহতায়ালার প্রেরিত বিধান অনুযায়ী আমাদের সমগ্র জীবন গড়ে তুলব। এবং দুনিয়ায় শান্তি, আখিরাতে মুক্তি ও চিরন্তন সুখের নীড় গড়ব?
জাহেলিয়াতের নতুন রণকৌশল
‘ইসলাম ও জাহেলিয়াতের চিরন্তন দ্বন্দ্ব’ শীর্ষক দীর্ঘ আলোচনায় এ কথা সুস্পষ্ট হয়েছে বলে মনে করি যে, সকল যুগে এ দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ চলেছে ইসলামের বিরুদ্ধে জাহেলিয়াতের। অর্থাৎ ইসলামের অনুসারী ও পতাকাবাহীদের বিরুদ্ধে ইসলাম বিরোধী শক্তিসমূহের। ইসলাম ও জাহেলিয়াত দুই বিপরীতমুখী শক্তি হওয়ার কারণ- একটির অস্তিত্ব ও প্রাধান্য অপরটির কাছে অসহনীয়। জাহেলিয়াত তার সর্বশক্তি প্রয়োগ করেও ইসলামকে নির্মূল করতে পারেনি। কারণ ইসলাম মহাসত্য ও মহাসুন্দর। সত্য ও সুন্দরের প্রতি মানব মনের আকর্ষণ সহজাত ও স্বভাবসুলভ। কিন্তু ইসলামের নবজাগরণ যেহেতু জাহেলিয়াতের জন্য অসহনীয় সেজন্যে জাহেলিয়াত এক নতুন স্ট্র্যাটেজি বা রণকৌশল অবলম্বন করে সাময়িকভাবে হলেও সাফল্য অর্জন করেছে। এ রণকৌশল সে সকল যুগেই অবলম্বন করেছে। ইসলাম ও মুসলমানদের ইতিহাস থেকে একথা প্রমাণিত যে, মুসলমানগণ ঐক্যবদ্ধভাবে ইসলামের রজ্জু দৃঢ়হস্তে আঁকড়ে ধরে থাকলে জাহেলিয়াত তাদের ধারেকাছেও ঘেঁষতে পারে না। তাই জাহেলিয়াত এ রণকৌশল অবলম্বন করে যে, মুসলমানের দ্বারাই ইসলামের উপর আঘাত হানতে হবে। জাহেলিয়াত স্বনামে ইসলামের উপর আক্রমণ করে বসলে মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে সে আক্রমণ প্রতিহত করার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু ইসলামের নাম নিয়ে কোন মুসলমান ইসলামের ক্ষতিসাধন করতে চাইলে মুসলিম ঐক্যে ফাটল সৃষ্টি হতে বাধ্য। ইসলামী খিলাফত ব্যবস্থার অবসানের পেছনে প্রচ্ছন্নভাবে উৎসাহ ও প্রেরণা সৃষ্টি করেছে জাহেলিয়াত এবং প্রকাশ্যে কাজ করেছে নামধারী মুসলমান। খিলাফত রাজতন্ত্রে রূপান্তরিত হওয়ার পর শাসনদণ্ড যাদের হাতে ছিল, তারা ইসলামী সুবিচার, ন্যায়নীতি, জানমালের নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত করার দিকে মনোযোগ দিতে পারেনি। ইসলামের প্রাণশক্তি জীবন্ত রাখার এবং মৌল শিক্ষা অক্ষুণ্ণ রাখার চেষ্টা করেছেন।
বিভিন্ন যুগে জাহেলিয়াতের অনুসারীগণ কতিপয় মুসলমানকে অর্থ ও পদমর্যাদায় প্রলুব্ধ করে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছে। এমনকি আলিম নামধারী কতিপয় লোককেও ইসলামের দুশমনগণ মুসলিম মিল্লাত ও ইসলামের বিরুদ্ধে কাজে লাগাতে সক্ষম হয়েছে।
সারা বিশ্বে জাহেলিয়াতের জয়ভেরী নিনাদিত হতে থাকে যখন দু’তিনটি ব্যতীত সকল মুসলিম দেশ ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শক্তির বশ্যতা স্বীকার করে নেয়। শাসকবৃন্দ বিজিত মুসলিম দেশগুলোতে সেকিউলার জীবনদর্শন ও শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করে মুসলমানদের মধ্যে ইসলামবিমুখ রাজনীতিবিদ ও বুদ্ধিজীবীর প্রজন্ম সৃষ্টি করে। পশ্চিমী শাসকবৃন্দ ইসলামী রীতিনীতি ও মূল্যবোধ যতোটুকু অবশিষ্ট ছিল তার উপর নিজেরা হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকে। তাদের চলে যাওয়ার পর যেসব মুসলমান তাদের স্থলাভিষিক্ত হয় তারা ইসলামের উপর ছুরিকাঘাত করতে থাকে। পাশ্চাত্যের ঔপনিবেশিক শাসন ও তাদের প্রবর্তিত সিক্ষাব্যবস্থা বহু ছোটো-বড়ো কামাল আতাতুর্ক, কর্নেল নাসের, আইয়ুব খান, সুকর্ন কায়েম করে।
নতুন প্রজন্মের এসব বিভ্রান্ত রাজনীতিক ও বুদ্ধিজীবী ইসলামের সংস্কার সাধনে ব্রতী হয়। শেখ মুহাম্মাদ আব্দুহু, স্যার সৈয়দ আহমদ, গোলাম আহমদ পারভেজ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ- পাশ্চাত্যের চিন্তাধারার সাথে সমন্বয় সাধন করে ইসলামকে নতুন ছাঁচে ঢেলে গড়ার প্রচারণা চালান। মির্জা গোলাম আহমদ তো এক নতুন ইসলামই আবিষ্কার করে বসেন। তবে ইসলামের মৌলিক বিধানগুলো পরিহার করে নারী-পুরুষের মিশ্র সমাবেশ, সহশিক্ষা, নাচগান, মদ্যপান, নারী স্বাধীনতার আন্দোলন আধুনিক শিক্ষিত মুসলমানদেরকে আকৃষ্ট ও প্রভাবিত করে। কোথাও ইসলামী পুনর্জাগরণের সম্ভাবনা দেখা দিলে অথবা কোথাও ইসলামী আন্দোলন চলতে থাকলে উপরোক্ত শ্রেণীর মুসলমান সর্বাগ্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। শুধু তা-ই নয়, শক্তি প্রয়োগ করে, ফ্যাসিবাদী কর্মকৌশল অবলম্বন করে, এমনকি হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে ইসলামী আন্দোলন নির্মূল করার সকল প্রচেষ্টা চালায়। এ কারণেই দুনিয়ার কোথাও সত্যিকার ইসলামী জীবন বিধান প্রতিষ্ঠার আন্দোলন সাফল্য লাভ করতে পারছে না।
জীবনের সকল স্তর ও বিভাগে পূর্ণাংগ ইসলামী জীবন বিধান প্রতিষ্ঠা জাহেলিয়াত তথা ইবলিসের কাছে সবচেয়ে অসহনীয়। তবে জীবনের অতি সংকীর্ণ পরিসরে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে খোদার কিছু স্তবস্তুতি, পূজা-অর্চনা যেমন- নামায, রোজা, কালেমার যিকির, কিছু দান-খয়রাত প্রভৃতিতে ইবলিসের কোন আপত্তি নেই। জীবনের বৃহত্তর ক্ষেত্রে- সমাজ, রাষ্ট্র ও শিক্ষাব্যবস্থায়, সভ্যতা-সংস্কৃতিতে, অর্থনীতি ও রাজনীতিতে তার আধিপত্য মেনে চললেই সে যথেষ্ট মনে করে। ইসলাম একটি পূর্ণাংগ জীবন বিধান হিসেবে কোথাও প্রতিষ্ঠিত হোক এটা যেমন ইবলিস বরদাশত করতে রাজি নয়- তেমনি বরদাশত করতে রাজি নয় তার একান্ত অনুগত দাস পাশ্চাত্য সভ্যতা সংস্কৃতির পতাকাবাহীগণ। তবে জাহেলিয়াতের আপাতঃ সাফল্য এটাই যে, ইসলাম-বিরোধিতার প্রকাশ্য সংগ্রামের প্রথম সারিতে সে তথাকথিত কতিপয় নামধারী মুসলমানকে দাঁড় করাতে সক্ষম হয়েছে। ইসলাম-বিরোধী রাষ্ট্রীয় শক্তিগুলো পেছনে থেকে অর্থ, উপায়-উপাদান, প্রেরণা ও সাহস যোগাচ্ছে। কিন্তু এতোসব সত্ত্বেও ইসলামী পুনর্জাগরণের প্রবল সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। সর্বত্র শিক্ষিত-চিন্তাশীল মানুষ এ সত্য উপলব্ধি করছে যে, সমস্যা জর্জরিত মানবসমাজের সকল সমস্যার সমাধান একমাত্র ইসলামেই রয়েছে। ইসলাম ছাড়া মানুষের সার্বিক কল্যাণ ও মুক্তির আর কোন পথ নেই।
এই সাথে এ সত্যটিও উপলব্ধি করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে যে, যে বস্তুটিকে কোন রোগের একমাত্র মহৌষধ বলে মেনে নেয়া হয়, তা অবশ্যই খাঁটি ও ভেজালমুক্ত হতে হবে। ভেজাল ঔষধ বার বার প্রয়োগেও রোগের কোন উপশম হয় না, বরঞ্চ রোগ বৃদ্ধির কারণ হয়। অতএব সর্বশেষ নবী কর্তৃক প্রচারিত প্রতিষ্ঠিত নির্ভেজাল ইসলামকেই বেছে নিতে হবে। তার মৌল শিক্ষার মধ্যে সামান্যতম পরিবর্তন-পরিবর্ধনও মেনে নেয়া যাবে না। এ ব্যাপারে বিশ্বনবী মুহাম্মাদ মুস্তাফার (সা) পরিপূর্ণ অনুসরণ ও অনুকরণ করতে হবে।
মজার ব্যাপার এই যে, ভেজাল ইসলামে জাহেলিয়াত বা ইসলামবিরোধীদের আপত্তির কোন কারণ নেই। তাওহীদের যে ব্যাখ্যা কুরআন ও হাদীসে আছে তা উপেক্ষা করে কবরপূজা ইত্যাদির মত শির্কমূলক কাজ করা, মানুষকে সার্বভৌম কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার অধিকারী মনে করা, পাশ্চাত্য জড়বাদী সভ্যতার অনুকরণ করা, সুদ-ঘুষ, ব্যভিচার, অন্যায়-অবিচার প্রভৃতির প্রশ্রয় দেয়া এবং এসবের উপরে ইসলামের লেবাস পরিয়ে দেয়া ইসলামবিরোধীদেরই অভিপ্রেত। আঞ্চলিকতা, স্বজনপ্রীতি, পক্ষপাতিত্ব, ভাষা, বর্ণ, গোত্র ও আভিজাত্যের ভিত্তিতে মানবজাতিকে বিভিন্ন দল উপদলে বিভক্ত করাই জাহেলিয়াতের কাজ। এসবের বিপরীত তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের বিশ্বাসের ভিত্তিতে সমাজ গঠনের প্রচেষ্টাই ইসলাম বিরোধী শক্তির চরম আপত্তির কারণ। জাহেলিয়াত এটাকেই মৌলবাদ বলে আখ্যায়িত করে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। এ যুদ্ধের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেছে ওসব মুসলিম শাসক ও তাদের অনুগ্রহপুষ্ট দলগুলো যারা নির্ভেজাল ইসলামকে তাদের স্বার্থের পরিপন্থী মনে করে। ইসলামের সাচ্চা সৈনিকগণও যুদ্ধের ময়দানে আছেন এবং অকাতরে জীবন দিচ্ছেন। আর এ যুদ্ধ নতুন নয়, কারণ ইসলাম ও জাহেলিয়াতের দ্বন্দ্ব সংঘর্ষও নতুন নয়। কারবালা থেকে বালাকোট পর্যন্ত সুদীর্ঘকাল যাবত চলেছে এ দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ। চলছে বালাকোটের পরেও এবং চলতেই থাকবে- যতোদিন না পূর্ণ বিজয় সূচিত হবে নির্ভেজাল ও বিশুদ্ধ ইসলামের।
চূড়ান্ত বিজয়ের জন্য প্রয়োজন
সর্বপ্রথম প্রয়োজন যে জিনিসের তা হচ্ছে এই যে, যাঁরা ইসলামের পুনর্জাগরণ দেখতে আগ্রহী, যাঁরা চান যে আল্লাহর সৃষ্ট যমীনের উপরে এবং মানবসমাজে একমাত্র আল্লাহরই পূর্ণাংগ আইন-শাসন কায়েম হোক, তাঁদের মধ্যে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। ঐক্যের উৎস হবে কুরআন ও সুন্নাহ এবং সাহাবায়ে কেরামের পারস্পরিক ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্ক হবে এ ঐক্যের আদর্শ ও প্রেরণার উৎস। জাহেলিয়াত যেন হানাফী-আহলে হাদীস, শাফেয়ী-হাম্বলী, দেওবন্দী-বেরেলভী প্রভৃতি নামে ইসলামপন্থীদেরকে শতধাবিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত করে রাখতে না পারে।
দ্বিতীয়তঃ ইসলাম ও তার কল্যাণকারিতা হৃদয়গ্রাহী ভাষায় সর্বশ্রেণীর জনগণের মধ্যে সুস্পষ্ট করে তুলে ধরতে হবে। আধুনিক খোদাহীন শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে ইসলাম সম্পর্কে যে ভুল ধারণার সৃষ্টি করা হয়েছে, তা দূর করতে হবে। ইসলামী শিক্ষার ব্যাপক প্রচার ও প্রসার ঘটাতে হবে।
তৃতীয়তঃ যেসব স্বৈরশাসন ইসলাম প্রতিষ্ঠার পথে প্রধান প্রতিবন্ধক, তা অপসারণের জন্যে সর্বাত্মক ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম পরিচালনা করতে হবে। এ ব্যাপারে নবী-রসূলগণের কর্মসূচিই অনুসরণ করতে হবে।
সর্বশেষে যেহেতু এ কাজ আল্লাহতায়ালার সাহায্য ব্যতীত কিছুতেই সম্ভব নয়, তার জন্যে তার সাথে অত্যন্ত গভীর ও নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। তার সন্তুষ্টির জন্যে সমগ্র জীবন বিলিয়ে দেয়ার মানসিকতা সৃষ্টি করতে হবে। এভাবেই বিশ্বনবীর নেতৃত্বে মদীনার বুকে ইসলামী কল্যাণরাষ্ট্রের ভিত রচিত হয়েছে। সে গৃহীত কর্মসূচি ও পন্থা-পদ্ধতি এখনো অবলম্বন করলে একই সুফল লাভ অত্যন্ত স্বাভাবিক।
উপসংহার
অত্র গ্রন্থে এ সত্যটি তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে যে, ইসলামকে নির্মূল করা, বিকৃত করা অথবা তার উপর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করাই জাহেলিয়াতের লক্ষ্য। এ লক্ষ্য থেকে সে কখনো বিচ্যুত হয়নি। তাই লক্ষ্য করা যায়, মানবজাতির সূচনা থেকেই সকল যুগে ইসলামের উপর জাহেলিয়াতের আক্রমণ অব্যাহত রাখা হয়েছে। বলতে গেলে মানবজাতির সমগ্র ইতিহাসটাই ইসলাম ও জাহেলিয়াতের সংঘাত-সংঘর্ষ ও জয়-পরাজয়ের ইতিহাস। কোন সময়ে ইসলাম বিজয়ী হয়েছে, কোন সময়ে জাহেলিয়াত।
এখন প্রশ্ন হলো এই যে, ইসলাম কি কোন পরাজয়ের বস্তু? অবশ্যই না। ইসলাম কখনো পরাজিত, নিশ্চিহ্ন ও নির্মূল হওয়ার বস্তু নয়। ইসলাম বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহতায়ালার দেয়া মানবজাতির জন্যে চিরসত্য, সুন্দর এবং মঙ্গলকর এক পূর্ণাংগ জীবনব্যবস্থা। এর প্রতি যারা বিশ্বাস পোষণ করে তারা মুসলিম বা মুসলমান নামে অভিহিত। মুসলমান যখন জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র ও বিভাগে পরিপূর্ণরূপে ইসলামী বিধান মেনে চলে, তার মন-মস্তিষ্কে, চিন্তাধারায়, রুচি ও মননশীলতায়, চরিত্র ও আচরণে, সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে ইসলামী আদর্শের প্রতিফলন ঘটায়, সর্বস্তরে মানুষ যখন ইসলামের অনুশাসন মেনে চলতে থাকে এবং একটি নির্মল, সুবিচারপূর্ণ ও সুশৃঙ্খল সমাজ কাঠামো গড়ে ওঠে, তখন একেই বলা হয় মুসলমান তথা ইসলামের বিজয়। পক্ষান্তরে মুসলমান যখন ইসলামী আদর্শ ও বিধান ভুলে যায় অথবা পরিহার করে অথবা যখন কোন দেশ ও জনপদের মানুষ ইসলাম প্রত্যাখ্যান করে, তখন ইসলামের, সত্য ও সুন্দরের পরাজয় হয় না, পরাজয় হয় ইসলাম বিস্মরণকারী মুসলমানের অথবা ইসলাম প্রত্যাখ্যানকারী মানুষের। এখন প্রশ্ন হলো এই যে, ইসলামের বাঁধন ও গাঁথুনি এতো মজবুত হওয়া সত্ত্বেও সেখানে জাহেলিয়াত প্রবেশাধিকার পায় কি করে। গ্রন্থে এ বিষয়ে কিছু ইঙ্গিত করা হয়েছে। জাহেলিয়াত তো সর্বাবস্থায় ইসলামের উপর আঘাত হানার জন্যে ওত পেতে বসে থাকে। তাই সুযোগ পেলে ইসলামের বিজয়ী অবস্থাতেও কোথাও এটি নির্দোষ ও নিরীহ আচার-অনুষ্ঠান হিসেবে, কোথাও ইসলামের রূপ ধারণ করে এবং কোথাও কোন ব্যক্তিত্বের প্রতি সীমাতিরিক্ত ভক্তিশ্রদ্ধার ভাবাবেগ সৃষ্টি করে ইসলামের পরিমণ্ডলে অনুপ্রবেশ করে। অতঃপর ধীরে ধীরে মানুষের মনে তার প্রভাব বিস্তার করে তাকে ইসলামের মৌল চিন্তা-চেতনা থেকে, মূলনীতি ও সত্য-সঠিক পথ (সিরাতুল মুস্তাকীম) থেকে একটু একটু করে বিচ্যুত করতে থাকে। অবশেষে ইসলাম থেকে তাকে বহুদূরে ঠেলে দিয়ে জাহেলিয়াত বিজয়ের জয়ধ্বনি করে। খিলাফতে রাশেদার শেষের দিকে ইসলামের পরিমণ্ডলে জাহেলিয়াতকে এভাবেই অনুপ্রবেশ করতে দেখা যায়।
পরবর্তীকালে এভাবেই জাহেলিয়াতকে সকলের অলক্ষ্যে একটি পচনশীল ক্ষত (CANCER) হিসেবে ইসলামের দেহে প্রবেশ করতে দেখা যায়। তাসাওউফের ময়দানে সুফি-সাধকগণ ভালো নিয়তে এবং খোদাপ্রেম লাভের উদ্দেশ্যে এমন কিছু অতিরিক্ত ক্রিয়াকর্ম (আমল) অবলম্বন করেন যা নবী করীম (সা) এবং সাহাবায়ে কেরাম (রা) না করলেও ইসলামের দৃষ্টিতে দূষণীয় বলে মনে করা হয়নি। কিন্তু কাল ও সময়ের ব্যবধানে তা বিকৃতির শিকার হয়ে ইসলামের দেহ কাঠামোতে পচনশীল ক্ষতের আকার ধারণ করেছে।
এ উপমহাদেশের প্রথম জিহাদী আন্দোলনের সিপাহসালার জাহেলিয়াতের সকল আবর্জনা দূর করে একটি সত্যিকার ও নির্মল ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র কায়েমের লক্ষ্যে জিহাদ করতে গিয়ে বালাকোটে শাহাদাতের অমৃত সাগরে অবগাহন করে জান্নাতবাসী হন।
উল্লেখ্য যে, ইসলাম মানুষকে ভালোবাসার শিক্ষা দেয়। যেহেতু স্রষ্টা আল্লাহতায়ালা স্বয়ং তাঁর সৃষ্টজীব মানুষকে ভালোবাসেন, তাই মানুষও মানুষকে ভালোবাসবে। তবে মানুষের প্রতি মানুষের ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার একটা সীমা নির্ধারিত করে দেয়া হয়েছে, যে সীমা কখনো লঙ্ঘন করা যাবে না। সর্বোচ্চ ভালোবাসার পাত্র স্বয়ং আল্লাহতায়ালা। তাঁর প্রতি মানুষের যে ভালোবাসা তা-ই হবে অন্যান্য সকল ভালোবাসার নিয়ামক। আপন জানমাল থেকেও অধিক ভালোবাসতে হবে আল্লাহকে এবং তাঁর ভালোবাসার জন্যেই অন্য আর সকলকে ভালোবাসা। আল্লাহর ভালোবাসার পর সর্বোচ্চ ভালোবাসার পাত্র আল্লাহর প্রিয় নবী মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম। আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা হবে সীমাহীন। কিন্তু নবীর প্রতি ভালোবাসার একটা সীমা নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। তা হচ্ছে এই যে, তা যেন সীমালঙ্ঘন করে তাঁকে আল্লাহর গুণাবলীতে ভূষিত না করে অর্থাৎ ‘উলুহিয়্যাতের’ তথা খোদায়ীর মর্যাদায় ভূষিত না করে। পূর্ববর্তী উম্মাতগণ এ সীমা লংঘনের ভুল করে পুরোপুরি পথভ্রষ্ট হয়েছে। আবার কোন অনবী মানুষই নবীর মতো ভালোবাসা পাওয়ার যোগ্য নয়। আবার পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের যে ভালোবাসা তা অন্য মানুষ পেতে পারে না। তবে আল্লাহর ভালোবাসার কষ্টিপাথরেই অন্যান্যের ভালোবাসার সীমা নির্ধারিত হবে।
ব্যক্তিত্বের প্রতি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা সীমা অতিক্রম করলেই তা ব্যক্তিপূজার সীমানার মধ্যে প্রবেশ করে এবং তা-ই জাহেলিয়াতের কাম্য। কোন ইসলামী আন্দোলনের সিপাহসালারকে তাঁর প্রাপ্য শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও মর্যাদা অবশ্যই দিতে হবে। কিন্তু তাঁর প্রতি সীমাতিরিক্ত ভালোবাসা ইসলামী আদর্শ ও মৌল বিশ্বাসের পরিপন্থী। জিহাদ বা ইসলামী আন্দোলন নিঃসন্দেহে আমীর বা নেতার নেতৃত্বাধীন। কিন্তু নেতার প্রতি সীমাতিরিক্ত শ্রদ্ধা-ভালোবাসা আন্দোলনের ক্ষতিসাধন করতে পারে যা কিছুতেই বাঞ্ছনীয় নয়।
উপমহাদেশের প্রথম জিহাদী আন্দোলনে সিপাহসালার হযরত সাইয়্যেদ আহমদ বেরেলভী এবং তাঁর সংগী-সাথী মুজাহিদগণ সকলে তাসাওউফপন্থী হওয়া সত্ত্বেও যুদ্ধের ময়দানে ও যুদ্ধ ছাউনিতে তাঁদের আচার-আচরণ সাহাবায়ে কেরামের আচার-আচরণেরই সাক্ষর বহন করে। কিন্তু মুজাহেদীনের মধ্যে অল্পসংখ্যক হলেও এমন কতিপয় ছিলেন, আমীরের প্রতি যাদের ভক্তিশ্রদ্ধা ছিল সীমাতিরিক্ত। যে কারণে তারা সাইয়্যেদ সাহেবের শাহাদাত বিশ্বাস করতে পারেননি। তাদের বিশ্বাস, তিনি লোকচক্ষুর অন্তরালে অবস্থান করছেন এবং অবশ্যই একসময়ে আত্মপ্রকাশ করবেন। এ ধরনের ধারণা-বিশ্বাস পোষণকারীগণ জিহাদ থেকে সরে পড়েন।
অতীতের সুফিয়ায়ে কেরামের কেউ কেউ তাদের দরবারে ‘সামা’ প্রথার প্রচলন করেন। ‘সামা’ আরবি শব্দ যার অর্থ শ্রবণ করা বা এমন কিছু যা শ্রবণ ও প্রণিধানযোগ্য। তাওহীদ ও রিসালাতের ভিত্তিতে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রশংসাসূচক কবিতা রচনা করা হতো এবং তা সুফিদের দরবারে সুমিষ্ট স্বরে গাওয়া হতো। যে দরবারে তা গাওয়া হতো সেখানে কোন বালক-বালিকা ও মেয়েলোক থাকতো না। কোন বাদ্যযন্ত্রও ব্যবহার করা হতো না। অত্যন্ত ভাবগম্ভীর পরিবেশে খোদাপ্রেম-রসে আপ্লুত ‘সামা’ সুমধুর কণ্ঠে গীত হতো এবং শ্রোতাগণ ভাবাবেগে তন্ময় হয়ে পড়তেন। এ ‘সামা’ দৃশ্যতঃ এবং অর্থগত দিক দিয়ে ইসলামবিরোধী না হলেও আল্লাহর শেষ নবী কর্তৃক অনুমোদিত ও প্রচলিত ছিল না বলে সুফিদের অনেকেই এটাকে গ্রহণ করতে পারেননি। মনে হয় সামারই বিকৃত রূপ বর্তমানে প্রচলিত ‘কাওয়ালী’।
কাওয়ালী বাদ্যযন্ত্রসহ গানের সুরে গাওয়া হয় নারী-পুরুষের মিশ্র সমাবেশে। এ কাওয়ালীর অনুষ্ঠান চলে সারা রাত ধরে। কাওয়ালী গায়ক (কাওয়াল) হন একজন পেশাদার শিল্পী। কাওয়াল এবং শ্রোতাগণ ইসলামের সাথে কমই সম্পর্ক রাখেন। অতিথি আপ্যায়নে ইসলামের সীমাও লঙ্ঘিত হয়।
এ ধরনের বহু আচার-অনুষ্ঠান ইসলামের লেবাস পরিধান করে ইসলামী আচার-অনুষ্ঠানের তালিকাভুক্ত হয়। এ সবই জাহেলিয়াতের কর্মকাণ্ড। ইসলাম ও ইসলামী সংস্কৃতিকে অবিকৃত ও কলুষমুক্ত রাখতে হলে ইসলাম ও জাহেলিয়াতের মাঝে এক সুদৃঢ় প্রাচীর নির্মাণ করে রাখতে হবে এবং প্রাচীরের কোন সূক্ষ্ম ছিদ্রপথেও যেন জাহেলিয়াত প্রবেশ করতে না পারে তার জন্যে সর্বদা সজাগ-সচেতন দৃষ্টি রাখতে হবে।
নিম্নের বিষয়গুলো জাহেলিয়াতের অন্তর্ভুক্তঃ আঞ্চলিকতা, বাপদাদার অনুসৃত ইসলামবিরোধী প্রথা, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নির্দেশাবলীর খেয়ালখুশি মতো ব্যাখ্যা করা, অমুসলিমদের সুখী ও সমৃদ্ধ জীবন দেখে দুঃখ করা এবং ইসলামকে তার প্রতিবন্ধক মনে করা, কবরপূজা, কবরের নামে মানত ও নযর-নিয়ায পেশ করা, পীরের অথবা যে কোন মানুষের ছবি শ্রদ্ধাসহকারে ঘরে রাখা, কবর অথবা কোন ইট-পাথরের স্তম্ভে মাল্যদান, অনৈসলামী নাম রাখা, কোন স্থানকে বায়তুল্লাহর মতো শ্রদ্ধেয় মনে করা এবং আখিরাতের নাজাতের জন্যে কোন মানুষের উপর নির্ভর করা প্রভৃতি জাহেলিয়াতের শামিল। এসবের ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।
উপমহাদেশের মুসলমান
মাঝের কিছুকাল বাদ দিলে ৭১১ খ্রিস্টাব্দে মুহাম্মাদ বিন কাসিমের সিন্ধু বিজয় থেকে ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ শাসন পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত হওয়া পর্যন্ত আট-ন’শ’ বছর মুসলিম শাসন চলেছে এ উপমহাদেশে। বিজয়ীর বেশে যারা এ উপমহাদেশে আগমন করেন তারা সকলেই ছিলেন বহিরাগত। কিন্তু তারা এ উপমহাদেশ থেকে প্রত্যাবর্তন করার অভিপ্রায়ে আসেননি, কোন সাম্রাজ্যবাদ বিস্তারের নেশায়, কোন ঔপনিবেশিক শাসন কায়েমের জন্যেও নয়। তারা এসেছিলেন এ দেশে একটা সুন্দর ও সুষ্ঠু শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা এবং পূর্ণ শান্তি-শৃংখলা ও নিরাপত্তা বিধানের জন্যে। তাদের সাথে আরও যে অসংখ্য লোক এসেছিলেন- সামরিক বাহিনীর লোক, ব্যবসায়ী, কবি-শিল্পী-সাহিত্যিক, জ্ঞানীগুণী তারা সকলেই এ দেশকে ভালোবেসে আপন দেশ মনে করে নিয়েছিলেন এবং এখানেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। তাদের বংশধরগণও তাদেরই পদাংক অনুসরণ করেছেন। তারা সকলে মুসলমান ও শাসক শ্রেণীভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও এ দেশের অমুসলিম অধিবাসীকে বলপ্রয়োগে ধর্মান্তরিত করার কোন চেষ্টাই করেননি। বরঞ্চ পারস্পরিক মধুর সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে পাশাপাশি শত শত বছর বসবাস করেছেন। একত্রে সুদীর্ঘকাল বসবাস করার পরেও মুসলমান ও অমুসলমান দু’টি সম্প্রদায় তাদের স্ব-স্ব জাতীয় স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে ফেলে একাকার হয়ে যায়নি।
কিন্তু একে অপরের প্রভাব গ্রহণ করেছে নিশ্চয়ই। পরিপূর্ণ ইসলামী জীবন যাপনের জন্যে যে ধরনের ইসলামী জ্ঞান ও প্রশিক্ষণের প্রয়োজন, তা অনেকের মধ্যেই ছিল না এবং ইসলামী মন-মস্তিষ্ক ও চরিত্র গঠনের কোন কর্মসূচিও তাদের ছিল না। তাই তাদের অনেকের মধ্যেই এ দেশীয় সাংস্কৃতিক প্রভাব কার্যকর হয় এবং বহু পৌত্তলিক আচার-অনুষ্ঠান ইসলামী লেবাস পরিধান করে মুসলিম সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। এভাবে জাহেলিয়াত আংশিকভাবে হলেও মুসলিম সমাজদেহে তার আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়। যার ফলে অনেক মুসলমান কয়েক শতাব্দী যাবত আধা-মুসলমান ও আধা-হিন্দুয়ানী জীবন যাপন করতে থাকে।
মুসলিম দেশগুলোতে ইউরোপীয় শাসনের প্রভাব
অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে নানান কারণে মুসলিম দেশগুলোর উপর ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শাসন কায়েম হতে থাকে। জাহেলিয়াত রাষ্ট্রীয় শক্তিসহ মুসলমানদের উপর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করে। ইউরোপীয় চিন্তাধারা, জীবনের দৃষ্টিভঙ্গি, মূল্যবোধ, জীবনদর্শন সবকিছুই মুসলমানদের মন-মস্তিষ্ক প্রভাবিত করতে থাকে। বিজয়ী শাসকদের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা বিজিত মুসলমানদেরকে ইসলাম থেকে দূরে নিক্ষেপ করতে থাকে। সে শিক্ষার বুনিয়াদ ছিল জড়বাদ, নাস্তিক্য, ধর্মহীনতা (SECULARISM) ও জাতীয়তাবাদ। এসবের ভিত্তিতেই পাশ্চাত্য সভ্যতা গড়ে ওঠে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এ সভ্যতাকে শক্তিশালী করে।
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে যে কোন ভালো বা মন্দ কাজে ব্যবহার করা যায়। বিশ্বের মুসলমান ইসলামী আদর্শে অবিচল থেকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির চর্চা করলে এ দুটোকে মানবতার কল্যাণে নিয়োজিত করতে পারতো। কিন্তু তারা ইসলাম থেকেও দূরে সরে পড়লো এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির চর্চায়ও মনোযোগ দিল না। তাদের এ দ্বিবিধ দুর্বলতার সুযোগে জাহেলিয়াতের পতাকাবাহী পাশ্চাত্য শক্তি তাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রভু হয়ে বসলো। মুসলমান চরম হীনমন্যতার শিকার হয়ে পড়লো। পাশ্চাত্য সভ্যতা, তাদের শিক্ষা ও রাজনৈতিক দর্শনকে (সেকিউলারিজম) মুসলমানগণ উন্নতি-অগ্রগতির চাবিকাঠি হিসেবে গ্রহণ করলো।
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মুসলিম দেশগুলো এক একটি করে গোলামির শিকল ছিন্ন করে স্বাধীনতা লাভ করতে থাকে। দুর্ভাগ্যের বিষয়, স্বাধীনতা লাভের পর শাসন ক্ষমতা তাদেরই হস্তগত হয় যারা ইসলামকে উন্নতি-অগ্রগতির অন্তরায় মনে করতো। ফলে জাহেলিয়াতের শাসন সর্বশক্তিসহ প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে এ শাসন কোন দেশেরই মুসলিম জনসাধারণ মেনে নিতে পারেনি। পাশ্চাত্য সভ্যতার মানসিক দাস শাসকগোষ্ঠী ব্যতীত দেশের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী ইসলামী জীবন বিধানের দাবিদার। তাই প্রায় সর্বত্র শাসক ও শাসিতের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ চলতেই থাকে, যার সমাপ্তি এখনো ঘটেনি।
সুখের বিষয়, সর্বত্র মুসলমানদের মধ্যে এবং বিশেষ করে শিক্ষিত যুবসমাজের মধ্যে ইসলামী প্রেরণার নবজোয়ার শুরু হয়েছে। ইসলামকে একটি পূর্ণাংগ জীবন বিধান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার আন্দোলনও চলছে। যুবসমাজের ইসলামী জিহাদী প্রেরণার যৌবনজোয়ার জলতরঙ্গে আফগানিস্তানে রাশিয়ার সামরিক শক্তি পরাজয়ে তলিয়ে গেছে। ফিলিস্তিনের মুক্তি আন্দোলনে ‘ইন্তিফাদা’ জিহাদী ঝাণ্ডা উত্তোলন করেছে। কাশ্মীরের মুক্তিপাগল মুসলমানও ভারত রাষ্ট্রের সকল দুঃশাসন ও নির্যাতন থেকে মুক্তির জন্যে সংগ্রাম করছে। জাহেলিয়াত নীরবে বসে নেই। এ তিনটি সংগ্রাম নস্যাৎ করার জন্যে ভারত, রাশিয়া ও আমেরিকার ক্রীড়নক হিসেবে ইরাকের সাদ্দাম হোসেন স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র কুয়েতকে জবরদখল করে একদিকে বিশ্বের মুসলিম ঐক্য বিনষ্ট করেন এবং অন্যদিকে ফিলিস্তিন, আফগানিস্তান ও কাশ্মীরের মুক্তি আন্দোলনের পৃষ্ঠে ছুরিকাঘাত করেন। ইসলাম ও জাহেলিয়াতের চিরন্তন দ্বন্দ্বে একটি মুসলিম রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান জাহেলিয়াতের ক্রীড়নকের ভূমিকা পালন করলেন। এটা ইসলামের ইতিহাসের এক চরম লজ্জাকর ঘটনা।
চিন্তার বিষয় এই যে, একটি মুসলিম দেশের মুসলিম সৈন্যবাহিনী কি করে আর একটি নিরপরাধ মুসলিম রাষ্ট্র জবরদখল করতে পারে, কি করে অসংখ্য নিরপরাধ মুসলিম নাগরিক হত্যা করতে পারে, তাদের ধনসম্পদ লুণ্ঠন করতে পারে, কি করে মুসলিম পর্দানশীন ও ধর্মভীরু মহিলাদের উপর পাশবিক অত্যাচার করে তাদের অমূল্য সম্পদ ইজ্জত-আব্রু লুট করতে পারে! মুসলমান নামধারী হলেও এসব নরপশু কি খোদা ও আখিরাতের প্রতি কোন বিশ্বাস পোষণ করে? এটাই তো মুসলমানদের উপর জাহেলিয়াতের তথা কুফরের এক ঐতিহাসিক বিজয়। ইসলামের অনুসারীগণ এর থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবেন কি? কারণ ইসলামের বিরুদ্ধে জাহেলিয়াতের আক্রমণ এমনি চলতেই থাকবে।
আশার আলোক
এ উপমহাদেশে বিগত শতাব্দীতে সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ বেরেলভীর (র) তাহরিকে মুজাহেদীন মুসলমানদের মধ্যে দুর্বার জিহাদী চেতনার সঞ্চার করে। ব্রিটিশ শাসকদের অমানুষিক ও লোমহর্ষক নির্যাতন নিষ্পেষণ মুসলমানদের মন থেকে জিহাদী চেতনা নির্মূল করতে পারেনি। ১৮৩১ সালে বালাকোটে সাইয়্যেদ আহমদ শহীদের শাহাদাতের একশ’ বছর পর নতুন করে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ তথা ইসলামী আন্দোলনের সূচনা হয়। এ আন্দোলন ১৯৪১ সালে জামায়াতে ইসলামী নামে একটি শক্তিশালী সংগঠনে রূপান্তরিত হয়। এ আন্দোলন ও সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা ও রূপকার ছিলেন বর্তমান বিশ্বের অন্যতম ইসলামী চিন্তাবিদ ও আলেমে দ্বীন মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল আ’লা মওদূদী (র)। তার তের বছর আগে (১৯২৮) ইখওয়ানুল মুসলিমুন নামে মিশরে একটি ইসলামী আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন শায়খ হাসানুল বান্না শহীদ (র)। বর্তমান বিশ্বের এ দু’টিই একমাত্র শক্তিশালী সুশৃঙ্খল ও সুসংহত সংগঠন যা সত্যিকার অর্থে ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে।
মিশরের ইসলামবিরোধী শাসকবৃন্দ ইখওয়ানুল মুসলিমুনের বহু নেতা-কর্মীকে ফাঁসির মঞ্চে ঝুলিয়ে, কারাপ্রাচীরের অভ্যন্তরে দৈহিক ও মানসিক নির্যাতন করে ধুঁকে ধুঁকে মরতে বাধ্য করে এবং শত শত নেতা-কর্মীকে দেশত্যাগ করতে বাধ্য করেই ক্ষান্ত হয়নি, বরঞ্চ সংগঠনকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে; যে নিষেধাজ্ঞা এখনো বলবৎ।
অপরদিকে জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তান, ভারত, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা এবং জম্মু-কাশ্মীর দেশগুলোতেই তার কর্মতৎপরতা সীমিত রাখেনি। এ আন্দোলনের বহু দায়িত্বশীল কর্মী গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছেন এবং সর্বত্র তারা বিভিন্ন নামে ইসলামী আন্দোলন পরিচালনা করছেন।
আশার বিষয়, বর্তমানে পৃথিবীর এমন কোন দেশ নেই যেখানে কোন না কোন প্রকারে ও নামে ইসলামী আন্দোলন ও ইসলামী সংগঠন পরিচালিত হচ্ছে না। ইখওয়ানুল মুসলিমুন ও জামায়াতে ইসলামীর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীবৃন্দ এসব আন্দোলনে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রধান প্রধান ভাষায় ইসলামের বিরাট সাহিত্য ভাণ্ডার গড়ে উঠেছে এবং সর্বত্র মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকলের মধ্যে ইসলামী জ্ঞান পরিবেশন করা হচ্ছে।
বিভিন্ন ধর্মের বিশেষ করে খৃস্টান, ইহুদী ও হিন্দু ধর্মের শিক্ষিত যুবক ও পণ্ডিত ব্যক্তি ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তার সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করছেন।
বলতে গেলে পৃথিবীর সর্বত্র ইসলামের পুনর্জাগরণ শুরু হয়েছে। পাশ্চাত্যের জড়বাদী মানবসমাজেও পরিবর্তন লক্ষ্যণীয়। অবাধ ভোগবিলাস, দিবারাত্রি মদ ও নারীর প্রেম সাগরে অবগাহন, যৌন অনাচার- এসবে কোন তৃপ্তি নেই, আনন্দ নেই, মনের প্রশান্তি নেই। ভোগের অতৃপ্ত লালসা-বাসনা মানুষকে অধিকতর ভোগের জন্যে অধীর ও চঞ্চল করে তোলে। ভোগের নেশায় সে ভুলে যায় জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। স্থায়ী ও স্থিতিশীল কোন কিছুর পরিবর্তে সে আঁকড়ে ধরে ক্ষণভঙ্গুরকে। অবশেষে তার জীবনটা নিজের কাছে হয়ে পড়ে এক বিরাট লায়াবিলিটি। এককালীন ভোগ-লালসার লেলিহান শিখা নিরাশা-দুরাশার লেলিহান শিখায় পরিণত হয়। জীবনের সুখ-শান্তির জন্যে যে পারিবারিক ব্যবস্থা, তাও ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়। মানসিক শান্তির অন্বেষায় সে তখন ছুটে বেড়ায় চারদিকে। তার জাগ্রত বিবেক বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ইসলামকেই বেছে নেয় শেষ অবলম্বন হিসেবে। সে উপলব্ধি করে ইসলামের প্রতি বিশ্বাসের অর্থ এমন এক শক্ত রজ্জু ধারণ করা- যা কোনদিন ছিন্ন হবার নয়। যার মধ্যে নেই কোন ব্যর্থতা, নেই কোন নৈরাশ্য। আছে পূর্ণ সাফল্য এবং জীবন সমস্যার সকল সমাধান। ইসলামের সুনিশ্চিত ঘোষণাঃ মৃত্যুর সাথে সাথে সবকিছু শেষ হয়ে যায় না, বরঞ্চ চিরন্তন আনন্দ ও সুখশান্তি অথবা দুঃখ-যাতনার এক নতুন জীবনের দ্বারোদঘাটিত হয়।
ইসলামের প্রতি বহুদিনের পুঞ্জীভূত বিদ্বেষ ও ভুল ধারণা যাদের মনে বদ্ধমূল তাদের হতাশা ছাড়া আর কিছু নেই। কিন্তু নিরপেক্ষ ও সুস্থ মন নিয়ে যারা ইসলাম সম্পর্কে জানবার কিছু চেষ্টা করছে তারাই আকৃষ্ট হয়ে পড়ছে এর বিশ্বজনীন আদর্শ ও শিক্ষার প্রতি। ইসলামকে একটি গতিশীল, চিরন্তন ও সর্বাংগ সুন্দর জীবন বিধান হিসেবে মেনে নিতে তারা দ্বিধাবোধ করছে না। ইসলামের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের এ এক সুস্পষ্ট নিদর্শন।
আফগানিস্তানে সাম্প্রতিককালে যে মুষ্টিমেয় মুজাহেদীনের কাছে চরম মার খেয়ে রাশিয়ার মতো বৃহৎ পরাশক্তি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করতে বাধ্য হয়েছে তা ইসলামেরই বিজয় ঘোষণা করছে। ইসলামী চেতনা ও প্রেরণার প্রচণ্ড তরংগাঘাতে রাশিয়ার লৌহপ্রাচীর নড়বড়ে হয়ে পড়ছে। ইসলামের পুনর্জাগরণ আজ রাশিয়ার কাছে সবচেয়ে ভীতিপ্রদ।
পাশ্চাত্যের দেশগুলোর প্রায় সকল শহরে ইসলামী আন্দোলনের কাজ শুরু হয়েছে। যে স্পেন থেকে একদা মুসলমানদেরকে নির্মূল করা হয়েছিল সেখানেও ইসলামের পুনর্জাগরণ শুরু হয়েছে। ইউরোপীয় দেশগুলো; আমেরিকা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, জাপান, সিংগাপুর, দক্ষিণ কোরিয়া, ফিলিপাইন, থাইল্যান্ড ও তাইওয়ানে বেশ কিছুকাল যাবত ইসলামী সংগঠন কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। সম্প্রতি মেক্সিকো, কোস্টারিকা, ইকুয়েডোর, আল সালভেদর, নিকারাগুয়া ও ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জে রীতিমত ইসলামী সংগঠন কায়েম হয়েছে। সকল স্থানে ইসলামী সেন্টার প্রতিষ্ঠিত করে ব্যাপকভাবে ইসলামী দাওয়াতের কাজ ছড়ানো হচ্ছে। আলহামদুলিল্লাহ। এসব আন্দোলনের উদ্যোক্তা বিভিন্ন দেশের ইখওয়ান ও জামায়াতে ইসলামীর কর্মীবৃন্দ। সর্বত্র এসব আন্দোলন ইসলামের উজ্জ্বল ভবিষ্যতেরই ইঙ্গিত বহন করছে।
জাহেলিয়াত তার সকল শক্তি ও অস্ত্র দিয়ে ইসলামের অগ্রগতি রুখবার চেষ্টা করছে। এখন ইসলামের বিজয় নির্ভর করছে মুসলমানদের ইসলামের প্রতি অবিচলতার উপর; ঐক্য, ত্যাগ ও কুরবানী এবং সহনশীলতার সাথে অবিরাম সংগ্রামের উপর। আল্লাহতায়ালার মদদ ব্যতীত কোন বিজয় সম্ভব নয়। তাই প্রতি মুহূর্তে পূর্ণ আনুগত্যের মাধ্যমে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারলেই তাঁর মদদ হবে নিশ্চিত এবং বিজয় হবে অতি সন্নিকট।
আল্লাহতায়ালা মুসলমানদের ঈমান ও বিবেক জাগ্রত করে দিন, ঈমানের হেফাজত করুন এবং জাহেলিয়াতের প্রতি-আক্রমণ প্রতিহত করার তাওফীক দান করুন- যেন ইসলাম একটি বিজয়ী শক্তি হিসেবে দুনিয়ার বুকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে।
।।সমাপ্ত।।
সুচীপত্রঃ
প্রকাশকের কথা
ইসলাম ও জাহেলিয়াত
সত্য ও মিথ্যা পরস্পর বিরোধী শক্তি
জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেক
জ্ঞান-বুদ্ধির সদব্যবহার
এ ব্যর্থতার কারণ কি?
আম্বিয়ায়ে কেরামের দাওয়াত
নবীগণের দাওয়াত ও জাহেলিয়াতের দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ
হযরত নূহ (আ)
আদ জাতি
সামূদ জাতি
লূত জাতি
হযরত লূতের কর্মক্ষেত্র
শুয়াইব জাতি
ফেরাউনের জাতি
ফেরাউন নামের অর্থ
বিশ্বনবীর আগমন
জাহেলিয়াতের আঁধারে আচ্ছন্ন পরিবেশ
অন্ধত্বের কারণ
জাহেলিয়াতপন্থীদের প্রতিক্রিয়া
কুরআন শ্রবণে বাধাদান
জাহেলিয়াতের মুকাবিলায় অবিচল থাকার উপায়
একঃ প্রকৃত বুদ্ধিমত্তা
দুইঃ ধন-দৌলত ও মর্যাদা সম্পর্কে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি
তিনঃ গোটা জীবনে ইসলামের অনুসরণ
চারঃ মানব জাতির ঐক্য
পাঁচঃ আইনের চোখে সকলে সমান
ছয়ঃ জিহাদের উদ্দেশ্য আল্লাহর কালেমা বুলন্দ করা
আল্লাহর পথে জান ও মালের ক্ষতি সত্যিকার লাভ
সাতঃ আল্লাহর পথে ব্যয়
ইসলামের একরূপতা ও একমুখীনতা
মুসলমানদের ঐক্য ও পরামর্শভিত্তিক সিদ্ধান্ত
জাহেলিয়াতের পুনরুত্থান
জাহেলিয়াতের চতুর্মুখী হামলা
নবুওতের উপর বিশ্বাস
নতুন ধর্মের প্রবর্তন
মিথ্যা নবীর পুনরাবির্ভাব
শির্ক ফিন্নবুওত
খিলাফত থেকে রাজতন্ত্র
খিলাফতে রাশেদার পর
অনৈসলামী তাসাউফ
জাহেলিয়াতের মারাত্মক অস্ত্র
সেকিউলারিজম
ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শাসনের অধীনে সেকিউলারিজম
প্রথম মহাযুদ্ধ
তাযকিয়ায়ে নফস (তাসাওউফ) ও রূহানিয়াত
মানবজীবনের উপর সেকিউলারিজমের প্রভাব
জাতীয়তাবাদ
গণতন্ত্র
জাহেলিয়াতের নতুন রণকৌশল
চূড়ান্ত বিজয়ের জন্য প্রয়োজন
উপসংহার
উপমহাদেশের মুসলমান
মুসলিম দেশগুলোতে ইউরোপীয় শাসনের প্রভাব
আশার আলোক

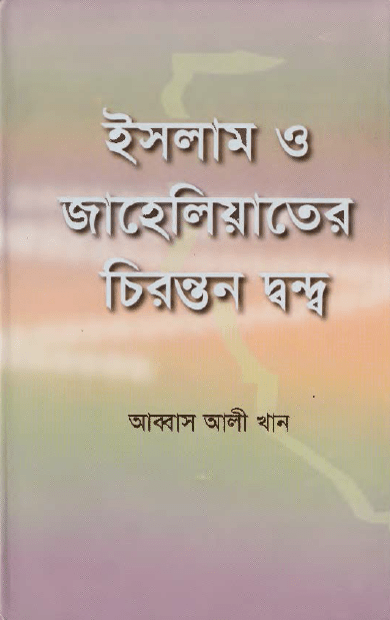 স্ক্যান কপি ডাউনলোড
স্ক্যান কপি ডাউনলোড