পূর্বকথা
ইসলাম মূলগতভাবে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ রাষ্ট্র-ব্যবস্থা।এই রাষ্ট্র-ব্যবস্থাকে বাস্তবে রূপদান করার সুমহান দায়িত্ব পালন করিয়াছেন খোদ ইসলামেরই মহানবী হযরত মুহাম্মাদ(স)। নবুয়্যতের সুদীর্ঘ তেইশ বৎসরে মানুষের সামষ্টিক জীবন সম্পর্কে যেসব আইন-কানুন ও বিধি-ব্যবস্থা অবতীর্ণ হইয়াছে, উহার সবকিছুকেই তিনি বাস্তবায়িত করিয়াছেন পুরাদস্তুর একটি রাষ্ট্রীয় কাঠামোর আওতায়। শাসন-প্রশাসন, আইন প্রনয়ন, সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষা, বিচার কার্য সম্পাদন,রাষ্ট্রীয় প্রতিরক্ষা বিধান ইত্যাকার প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ কাজই তিনি সম্পাদন করিয়াছেন সেই একই আইন-কানুন ও বিধি-ব্যবস্থার আলোকে। এইভাবে ইসলামি রাষ্ট্র-ব্যবস্থার একটি স্থায়ী বুনিয়াদ তিনি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন নবুয়্যতের তেইশ বৎসরেই।
মহানবী(স)-র তিরোধানের পর সেই স্থায়ী বুনিয়াদের উপরই গড়িয়া উঠিয়াছে ইসলামের আদর্শ রাষ্ট্র- ব্যবস্থা- খিলাফতে রাশেদা। হযরত আবূ বকর,হযরত উমর, হযরত উসমান,হযরত আলী(রা)- মহানবী(স)-র এই চার ঘনিষ্ঠ সহচর পরম যত্নে ও মমতায় বিন্যস্ত ও বিকশিত করিয়া তুলিয়াছেন নবুয়্যতি ধারার এই রাষ্ট্র-ব্যবস্থাকে। শুধু তাহাই নহে,ইহার পরিধিকে তাঁহারা সম্প্রসারিত করিয়াছেন আরব উপদ্বীপের সীমানা অতিক্রম করিয়া গোটা ইরান ও রোমান সাম্রাজ্যর বিশাল অঞ্চল জুড়িয়া। বস্তুতঃ মানব জাতির ইতিহাসে একমাত্র এই রাষ্ট্র-ব্যবস্থাই যে স্বর্ণোজ্জল অধ্যায় রচনা করিতে পারিয়াছে, তাহা অকাট্যরুপে প্রমাণিত হইয়াছে। আধুনিক রাষ্ট্র-বিজ্ঞানীরা যত চমকপ্রদ তন্ত্রমন্ত্রই উদ্ভাবন করিয়া থাকুন না কেন, মানবতার কল্যাণ সাধনে নবুয়্যতী ধারার এই খিলাফতের ন্যায় বিপুল সাফল্য কোন পদ্ধতিই আর অর্জন করিতে পারে নাই, ইহা এক ঐতিহাসিক সত্য।
দুর্ভাগ্যবশতঃনবুয়্যতী ধারার এই খিলাফত দুনিয়ার বুকে টিকিয়া ছিল মাত্র তিরিশ বৎসর। ইহার পরই রাজতন্ত্র ও স্বৈরতন্ত্রের অভিশাপ নামিয়া আসিয়াছে গোটা মুসলিম জাতির উপর। জাহিলিয়াতের অন্ধকার যবনিকা ঢাকিয়া দিয়াছে তাহাদের সোনালি ভবিষ্যৎকে। বর্তমানে উহারই জের চলিতেছে মুসলিম জাহানের দেশে দেশে। তদুপরি সাম্প্রতিককালে ইহার সহিত যুক্ত হইয়াছে পশ্চিমের ইহুদী-খৃস্টানদের উদ্ভাবিত গনতন্ত্র নামক একটি নব্য জাহিলিয়াত। ইহার বিষময় পরিণতি গোটা মুসলিম জাহানকে আজ নিক্ষেপ করিয়াছে রাজনৈতিক সংকটের ঘূর্ণাবর্তে। আধুনিক কালের তন্ত্রমন্ত্রগুলি তাহাদের কোন সমস্যার সমাধান করা তো দূরের কথা, বরং নূতন নূতন সমস্যার জন্ম দিয়া গোটা মুসলিম সমাজকে ব্যাধিগ্রস্ত করিয়া তুলিতেছে।
এই পরিস্থিতিতে আজ মুসলিম সমাজে ইসলামের আদর্শ রাষ্ট্র-ব্যবস্থা-খিলাফতে রাশেদা সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনার প্রয়োজন অত্যন্ত তিব্রতর হইয়া উঠিয়াছে। মুসলমানদের সকল রাজনৈতিক ব্যাধির একমাত্র নিরাময় যে নবুয়্যতী ধারার খিলাফত, অন্ন কোন তন্ত্রমন্ত্র নয়- এ সত্যটি আজ মুসলিম সমাজের নিকট উদ্ভাসিত করিয়া তোলা একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। মহান ইসলামী চিন্তাবিদ ও দার্শনিক হযরত মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম(রহ) এই প্রয়োজনের তাগিদেই “খিলাফতে রাশেদা” নামক বর্তমান গ্রন্থটি রচনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থে তিনি গতানুগতিক ধারায় ইসলামের চারি খলিফার জীবন-বৃতান্তের উপর খুব বেশি আলোকপাত করেন নাই, বরং তাঁহাদের শাসন-প্রশাসনের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য ও অনুকরণীয় দিকগুলিই যথাসম্ভব বিস্তৃতরুপে তুলিয়া ধরার প্রয়াস পাইয়াছেন। এই দিক দিয়া বাংলাভাষার খিলাফতে রাশেদা সম্পর্কে ইহা একখানি অভিনব গ্রন্থ।
১৯৭৫ সন হইতে ১৯৮০ সন পর্যন্ত গ্রন্থটির দুইটি সংস্করন প্রকাশিত হওয়ার পর গ্রন্থকার নিজেই ইহার নানা অংশ ব্যাপকভাবে পরিমার্জন করিয়াছেন। বর্তমান সংস্করণে মুদ্রণ প্রমাদ্গুলির সংশোধন ছাড়াও ইহাতে অনেক প্রাসঙ্গিক তথ্য সংযোজিত হইয়াছে। ইহাতে গ্রন্থটির সৌকর্য আরো বৃদ্ধি পাইয়াছে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস,গ্রন্থটির বর্তমান সংস্করণ বাংলাভাষী পাঠকদের নিকট অধিকতর সমাদৃত হইবে এবং এদেশের দিকভ্রষ্ট জনগণকে সঠিক পথ-নির্দেশ করিতে বিপুল অবদান রাখিবে।
মহান আল্লাহ গ্রন্থকারের এই দ্বীনী খেদমত কবুল করুন এবং ইহার বিনিময়ে তাঁহাকে জান্নাতুল ফেরদৌসে স্থান দিন, ইহাই আমাদের সানুনয় প্রার্থনা।
মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান
চেয়ারম্যান
মওলানা আবদুর রহীম ফাউন্ডেশন
ঢাকা জুলাই,১৯৯৫
শুরু কথা
ইসলামের পুর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা সম্পর্কে ব্যাপক অধ্যয়ন,চিন্তা-গবেষণা-পর্যালোচনা ও গ্রন্থ প্রণয়ন পর্যায়ে উহার বাস্তব রুপ দানের কাজে আত্মনিয়োগ করার প্রেরনা স্বাভাবিকভাবেই আমার মনে জাগিয়া উঠিয়াছিল।বিশেষতঃ রাসূলে কারীম(স) আল্লাহ্ তায়ালার সর্বশেষ নবী ও রাসূল হিসাবে যে আদর্শিক বিধান উপস্থাপন করিয়াছিলেন তাহা নিছক একটি আদর্শবাদেরই ব্যাপার ছিল না বরং তাহা ছিল পূর্ণ মাত্রায় একটি বাস্তব জীবন-ব্যবস্থা ও সমাজ গঠনের সফল কার্যসুচী। তিনি আল্লাহ্ তা’আলার নিকট হইতে যাহা কিছুই পাইয়াছেন, তাহাই তিনি বাস্তবায়িত করিয়াছেন। ইহাই ছিল তাঁহার স্বাভাবিক কর্মধারা। তিনি যখন দুনিয়া হইতে চির বিদায় লইয়া চলিয়া গেলেন, তখন একদিকে তিনি রাখিয়া গেলেন তাঁহার নিজ হস্তে পূর্ণ প্রযত্নে সংকলিত আল্লাহ্র বাণী-কুরআন মজিদ ও তাঁহার আজীবনের সংগ্রাম-সাধনার ফসল একটি রাষ্ট্র ও সমাজ। কুরআন ও সুন্নাত গ্রন্থাকারে আমাদের সামনে চির সমুজ্জ্বল হইয়া আছে,চিরকালই তাহা থাকিবে। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র ও সমাজের সঠিক চিত্রও রহিয়াছে ইতিহাসের পৃষ্ঠায়।তবে বাস্তবে উহার অস্তিত্ব বর্তমানে নাই বলিলেও চলে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও সাধারণভাবে দুনিয়ার সুস্থ বিবেকসম্পন্ন ও সুক্ষ চিন্তাশীল লোকদের নিকট এবং বিশেষভাবে ইসলাম ও রাসূলের প্রতি ইমানদার লোকদের নিকট রাসূলে কারীম(স)-এর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থা বর্তমান কালেও প্রেরনার অন্যতম প্রধান উৎস। ইহা তাঁহাদের নিকট এখনও আদর্শিক লক্ষ্যস্থলে পরিণত হইয়া আছে এবং চিরকালই তাহা থাকিবে,ইহা সন্দেহাতীত কথা।
নবী করীম(স) যে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন,তাঁহার ইন্তেকালের পর হইতে স্বয়ং তাহাঁরই ঘোষণানুযায়ী উহার নূতন নামকরণ করা হইয়াছেঃ “খিলাফতে রাশেদা”। খিলাফতে রাশেদা বাস্তবতঃতাহাই, যাহা আদর্শগতভাবে কুরআন ও সুন্নাহ বিধৃত, রাসূলে করীম(স) নিজে তাঁহার তেইশ বছরের নবুয়্যাতী জীবনে অবিশ্রান্ত সাধনা ও সংগ্রামের ফলে যে রাষ্ট্র ও সমাজ গঠন করিয়া চালাইয়া গিয়াছেন, খিলাফতে রাশেদা উহারই জের-উহারই দ্বিতীয় অধ্যায়। কুরআন ও সুন্নাহ যদি বীজ হয়, তাহা হইলে “ খিলাফতে রাশেদা” উহার শাখা-প্রশাখা, পত্রপল্লব ও ফুলে ফলে সুশোভিত পুর্নাঙ্গ বৃক্ষ। আর রাসূলে করীম(স)-এর আমল হইল এই বৃক্ষের কাণ্ড বিশেষ। এই পর্যায়ে আমি ব্যাপক অধ্যয়ন ও চিন্তা-গবেষণা চালানো এবং ইহার সঠিক চিত্র বাংলা ভাষায় উদ্ভাসিত করিয়া তোলার সিদ্ধান্ত গ্রহন করি- সে আজ বিশ বছর পূর্বের কথা।অতঃপর বিভিন্ন সময় যতটুকু কথা ও যেসব দিক আমার নিকট স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, তখন ততটুকুই প্রবন্ধাকারে লিখিয়া প্রকাশ করিয়াছি।ইহা গ্রন্থরুপে প্রকাশের ব্যবস্থা হওয়ার পরও ইহার পূর্ণতা বিধানের জন্য কয়েকটি দিক সম্পর্কে আমাকে লেখনী চালাইতে হইয়াছে। ফলে “খিলাফতে রাশেদা” এক সঙ্গে ধারাবাহিকভাবে লিখিত কোন গ্রন্থ হয় নাই-হইয়াছে বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন পর্যায়ে লিখিত এবং প্রকাশিত-অপ্রকাশিত রচনাবলীর সমন্বয়। তবু শেষ পর্যন্ত ইহা গ্রন্থাকারে পাঠকদের নিকট পেশ করা সম্ভব হইতেছে দেখিয়া আল্লাহ্ তা’আলার লাখ লাখ শোকর আদায় করিতেছি।
১৯৭৫ সনের জানুয়ারী মাসে এই গ্রন্থখানি সর্বপ্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল।অল্প সময়ের মধ্যে ইহা নিঃশেষ হইয়া যাওয়ার পর ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হয় ১৯৮০ সনের জুলাই মাসে।ইহা আল্লাহ্র অশেষ মেহেরবানী।
আশা করি আমার অন্যান্য গ্রন্থের ন্যায় এই গ্রন্থখানিও বিদগ্ধ সমাজে সমাদৃত হইবে এবং আদর্শবাদের ক্ষেত্রে এক নূতন প্রেরণার সূত্রপাত হইবে।
-মুহাম্মদ আবদুর রহীম
(ক)
রাসূলেকরীম(স) বলিয়াছেনঃ
**********(আরবী)
আমার পরে তোমাদের মধ্যে যাহারাই জীবিত থাকিবে, তাহারা বহু মতবিরোধ দেখিতে পাইবে। এইরুপ অবস্থায় তোমাদের কর্তব্য হইবে আমারই আদর্শ এবং হেদায়েতপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদুনের আদর্শ গ্রহন করা।তোমার উহা শক্তভাবে ধারন করিবে-কিছুতেই ছাড়িয়া দিবে না।(মুসনাদে আহমাদ,তিরমিযি,ইবনে মাযাহ)
(খ)
একটি দীর্ঘ হাদিসে কুদসীতে রাসূলে করীম(স)-এর পরিচয় ও প্রশংসা উল্লেখের পর তাঁহার সাহাবীদের পরিচয় স্বরূপ আল্লাহ্ তা’আলার এই কথাগুলি উদ্ধৃত হইয়াছেঃ
*******(আরবী)
হযরত মুহাম্মাদের উম্মত তাঁহার অন্তর্ধানের পর মহান সত্যর দিকে আহ্বান জানাইবে এবং সত্যদ্বীন সহকারে সুবিচার ও ইনসাফ করিবে। যাহারা তাহাদের সাহায্য করিবে আমি তাহাদিগকে সম্মানিত করিব।যাহারা তাহাদের জন্য দোয়া করিবে আমি তাহাদিগকে সাহায্য দিব। যাহারা তাহাদের বিরুদ্ধতা করিবে কিংবা তাহাদের উপর বিদ্রোহ করিবে, অথবা তাহাদের হাতের কোন জিনিস কাড়িয়া লইতে ইচ্ছা করিবে তাহাদিগকে চরম অকল্যাণ দ্বারা পরিবেষ্টিত করিয়া ফেলিব।প্রথমোক্ত লোকদিগকে তাহাদের নবীগণের উত্তরাধিকারী বানাইব,তাহাদিগকে আল্লাহ্র দিকে আহ্বানদাতা বানাইব। তাহারা সত্য ও ন্যায়ের আদেশ করিবে এবং অন্যায় ও মিথ্যা হইতে নিষেধ করিবে। তাহারা নামায কায়েম করিবে,যাকাত আদায় করিবে,ওয়াদা পূর্ণ করিবে আমি তাহাদেরপ্রথম পর্যায়ের লোকদের দ্বারা যে কল্যাণের সূচনা করিয়াছি, তাহাদের দ্বারাই সেই কল্যাণকে পরিসমাপ্ত করিব। ইহা একান্তভাবে আমারই অনুগ্রহের ব্যাপার। যাহাকে ইচ্ছা আমি তাহাকেই এই অনুগ্রহ দেই। আর প্রকৃতপক্ষে আমি মহান অনুগ্রহকারী।(ইবনে আবু হাতিম-অহব ইবনে মুনাব্বাহ হইতে ইবনে কাসীর-তাঁহার তাফসীরে।)
ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা
বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ(স) আল্লাহ্ তা’আলার সর্বশেষ নবী ও রাসূল হিসাবে দুনিয়ায় প্রেরিত হইয়াছিলেন। দুনিয়ায় তাঁহার উপর যে দায়িত্ব অর্পিত হইয়াছিল,ইসলামী পরিভাষায় সেই দায়িত্তের সরূপকে এক কথায় বলা যায়ঃ “ইক্কামতে দ্বীন”। আল্লাহ্র দ্বীন পুর্নাঙ্গরুপে কায়েম করাই ছিল সর্বশেষ নবীর মৌলিক দায়িত্ব। এই বাক্য হইতে স্বতঃই স্পষ্ট হইয়া উঠে যে, তিনি “দ্বীন” নিজে রচনা করেন নাই, আল্লাহ্র নিকট হইতে গ্রহন করিয়াছেন। এই “দ্বীন”অহীর মাধ্যমেই তাঁহার প্রতি আল্লাহ্র নিকট হইতে নাজিল হইয়াছে। এই হিসাবে তিনি আল্লাহ্র রাসূল। আল্লাহ্র নিকট হইতে পাওয়া “অহী” মৌলিক প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে উহার যথাযথ ব্যাখ্যা দান এবং নিজের জীবনে বাস্তব অনুসরণের মাধ্যমে উহাকে সমুদ্ভাসিত করিয়া তোলাও ছিল নবী-রাসূল হিসাবেই তাঁহার দায়িত্তের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু “ইক্কামতে দ্বীন”-এর জন্য এইটুকু কাজই যথেষ্ট ছিলনা,আল্লাহ্র নাজিল করা আইন-বিধানকে ব্যক্তি জীবনে ও সমাজ-সমষ্ঠির সার্বিক ক্ষেত্রে পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত করাও ছিল নবী-রাসূল হিসাবেই তাঁহার কর্তব্য। এই কারণে তাঁহাকে যে দ্বীনী দাওয়াতী প্রচেষ্টা চালাইতে হইয়াছে, তাহাই বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করিয়া একটি পুর্নাঙ্গ রাষ্ট্ররূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। এই হিসেবে তিনি ইসলামী রাষ্ট্রের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা এবং উহার জনগণের একচ্ছত্র নেতা ও রাষ্ট্রপ্রধান।
আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে রাষ্ট্র বলিতে যাহা বুঝায়,নবী করীম (স)-এর সাধনা-সংগ্রামের পরিণতিতে সেই জিনিসেরই পূর্ণ প্রতিফলন বিদ্যমান।“রাষ্ট্র” একটি রাজনৈতিক সংস্থা। মানব জীবনের প্রয়োজন পরিপূরণের উদ্দেশ্য এই সংস্থাটি গড়িয়া তোলা হয় এবং জীবনকে কল্যাণময় ও উন্নততর করিয়া তোলার জন্য ইহার অস্তিত্ব অক্ষুন্ন ও স্থায়ী করিয়া রাখা হয়।“রাষ্ট্র”মানব-শক্তির উন্নততর ফসল। যেখানে মানব জাতির একটা বিরাট সংখ্যা-সমষ্ঠি সাধারনতঃএকটা নির্দিষ্ট ভৌগলিক অঞ্চলের দখলদার এবং বহু সংখ্যক লোকের একটা নির্দিষ্ট সংখ্যক শ্রেণীর ইচ্ছা তাহাদের সম্মিলিত শক্তির কারণে উহার বিরুদ্ধবাদীদের দমন-উদ্দেশ্য কার্যকর হইতে পারে; সেখানেই রাষ্ট্র অস্তিত্বশীল। আর সংক্ষিপ্ত ভাষায়, কোন বিশেষ ভূ-খণ্ডের রাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে গড়িয়া উঠা জাতীয় সত্তাকেই বলা হয় রাষ্ট্র বা State।
রাষ্ট্রবিজ্ঞান প্রদত্ত এই সংজ্ঞাসমূহ হইতে নিম্নোক্ত চারটি জিনিসই রাষ্ট্রের মৌল উপকরণ রূপে প্রমাণিত হইয়াছেঃ(১)জনতা(population),(২)নির্দিষ্ট ভূখন্ড(Territory),(৩)সার্বভৌমত্ব(Sovereignty)এবং (৪)প্রশাসন যন্ত্র বা সরকার(Government)।
রাসূলে করীম(স)-এর মদীনায় উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত তাঁহার দায়িত্ব পালন প্রচেষ্টার যে ফসল ফলিয়ছিল, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে সুক্ষাতিসুক্ষ বিচার-বিবেচনায়ও তাহাতে এই চারটি মৌল উপকরণ পূর্ণমাত্রায় বর্তমান ছিল-যদিও দৃষ্টিকোণ ও মৌল ভাবধারার দিক দিয়া উহার স্বরূপ ছিল অন্যান্য সব রাষ্ট্রবিজ্ঞান হইতে সম্পূর্ণ ভিন্নতর।
রাষ্ট্রের প্রথম ভিত্তিস্থাপন
নবী করীম(স) আল্লাহ্র রাসূল ও নবীরুপে মনোনীত হওয়ার পর দ্বীন-ইসলামের যে বিপ্লবাত্মক আদর্শ প্রথমে গোপনে এবং পরে প্রকাশ্য প্রচার করিতে শুরু করিয়াছিলেন, তাহাতে তদানীন্তন কুরাইশদের ধর্মমত, নৈতিক চরিত্র, অর্থ ব্যবস্থা এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে প্রবল প্রতিক্রিয়া সূচিত হইয়া ছিল। সত্য কথা এই যে, ইহার দরুণ তাহাদের সর্ব প্রকার স্বার্থ ও আশা-আকাঙ্খা এক কঠিন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হইয়া পড়িয়াছিল। এই কারণে কুরাইশরা নবী করীম(স) এবং তাঁহার প্রতি ইমানদার মুসলমানদের জীবনকে দুঃসহ অত্যাচার ও নিপীড়নে জর্জরিত করিয়া তুলিয়াছিল। শেষ পর্যন্ত তিনি আল্লাহ্ তা’আয়ালার নির্দেশানুক্রমে মক্কা ত্যাগ করিয়া মদিনায় চলিয়া যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহন করেন। এই সময় নবী করীম(স) হজ্জ উদযাপন উদ্দেশ্য আগত মদিনার মুসলমানদের নিকট হইতে দুই-দুইবার আনুগত্যর “বায়’আত”১ {শব্দটির ব্যবহারিক ও পারিভাষিক অর্থ “আনুগত্যর শপথ”।} ইতিহাসে এই “বায়আত”দুইটি “প্রথম আকাবা-বায়’আত”ও “দ্বিতীয় আকাবা-বায়’আত”২{‘আকাবা’ বায়’আতের পূর্ণ বিবরণ এইরূপঃ মদীনার লোকেরা রাত্রির তৃতীয় প্রহরে ‘আকাবা’ নামক স্থানে সমবেত হইয়া রাসূলে করীম(স)-এর আগমন প্রতীক্ষায় উদগ্রীব। একটু পরেই নবী করীম(স) তাঁহার চাচা আব্বাসকে(তিনি তখন ইসলাম গ্রহন করেন নাই)সঙ্গে লইয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন।প্রথমেই আব্বাস বলিলেনঃ হে খাজরাজ গোত্রের লোকের! তোমরা ভাল করিয়াই জান, মুহাম্মদ (স) আমাদের মধ্যে অত্যন্ত সম্মানিত ও মর্যাদাবান ব্যক্তি। তাঁহার শত্রুদের হইতে আমারাই তাঁহার সংরক্ষক। কিন্তু এক্ষণে তিনি নিজেই এই শহর(মক্কা) ত্যাগ করিয়া তোমাদের সহিত মিলিত হওয়ার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কেননা তোমরা তাঁহাকে নিজেদের শহরে আহ্বান জানাইতেছ। তোমরা যদি তাঁহার পূর্ণ সংরক্ষনে শক্তিশালী হইয়া থাক এবং তাঁহার শত্রুদের হাত হইতে তাঁহাকে রক্ষা করার সাহস তোমাদের থাকে, তাহা হইলে তোমরা ইহা কর। অন্যথায় এখনি তোমাদের ‘না’ বলিয়া দেওয়া উচিৎ। কেননা মুহাম্মাদ এখন তো আমাদের হেফাজতে আছেন। তোমরা তাঁহাকে লইয়া গিয়া শত্রুদের হাতে ছাড়িয়া দিবে- এমনটি যেন না হয়। তাঁহারা বলিলেন, ‘আমরা আপনার কথা শুনিয়াছি। এখন সে রাসূল, আপনার বক্তব্য বলুন। আল্লাহ্র বিধান কিংবা আপনার নিজের সম্পর্কে আমাদের নিকট হইতে যদি কোন প্রতিশ্রুতি লইতে হয়, তবে তাহা গ্রহন করুন। ইহার পর নবী করীম(স) প্রথমে কুরআন মজিদের অংশ বিশেষ পাঠ করিলেন। আল্লাহ্র বন্দেগী কবুল করার এবং তাঁহার সহিত শিরক না করার শর্ত পেশ করিলেন। অতঃপর বলিলেনঃ ‘আমি তোমাদের নিকট হইতে প্রতিশ্রুতি লইতেছি যে, তোমরা আমার সাহায্য সহযোগিতা ও সমর্থন এমনভাবে করিবে,যেমন তোমরা তোমাদের স্ত্রীলোকদের ও তোমাদের সন্তানদের করিয়া থাক’। ইহার সঙ্গে সঙ্গে রাসূলে করীম(স)-এর হাত ধরিয়া তাঁহারা বলিয়া উঠলেনঃ ‘হ্যাঁ,সেই মহান সত্তার শপথ,যিনি আপনাকে সত্য-সঠিক দ্বীনসহ পাঠাইয়াছেন,আমরা এমনিভাবেই আপনার সহায়তা ও সংরক্ষণ করিব, যেমন আমরা আমাদের পরিবারবর্গের করিয়া থাকি’। অতঃপর সকলেই সমবেতভাবে বলিলেনঃ ‘আমরা প্রতিশ্রুতি দিতেছি, আমরা সর্বাবস্থায় আপনার কথা শুনিব, আপনার আনুগত্য স্বীকার করিব- দুঃখ-বিপদ,স্বাচ্ছন্দ্য-সচ্ছলতা কিংবা অভাব-অনটন যাহাই হউক না কেন আর আমরা যেখানেই থাকি না কেন, আমরা সর্বসময় ও সর্বাবস্থায় সত্য বলিব;কাহাকেও ভয় করিব না এবং কোন উৎপীড়নেরও পরোয়া করিব না।
অতঃপর তাঁহার বলিলেনঃ ‘আমাদের মনে একটা প্রশ্ন জাগিতেছে। এমন তো হইবে না যে, আল্লাহ্ তা’আলা যখন আপনাকে বিজয় দান করিবেন,তখন আপনি আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া আপনার নিজের জাতির লোকদের সহিত মিলিত হইয়া যাইবেন’? ইহা শুনিয়া নবী (স) স্মিত হাসি হাসিলেন এবং বলিলেনঃ
*******(আরবী)
না,এ বিষয়ে তোমরা নিশ্চিন্ত থাক। তোমরা যাহার সহিত লড়াই করিবে,আমিও তাহাদের সহিত লড়াই করিব। তোমরা যাহাদের সহিত সন্ধি করিবে আমিও তাহাদের সহিত সন্ধি করিব। তোমাদের দায়িত্ব আমার দায়িত্ব। তোমাদের মর্যাদা-সম্ভ্রম আমার মর্যাদা ও সম্ভ্রম রুপে গণ্য হইবে। আর আমার জীবন ও মরন তোমাদের সঙ্গেই হইবে।
বস্তুতঃ আকাবায় এইরুপ কথোপকথনের মাধ্যমে প্রকারান্তরে একটি সামাজিক-সামষ্ঠিক চুক্তিই সম্পাদিত হইয়াছিল। ইহার মাধ্যমে মদিনাবাসীরা রাসূলে করীম(স)-কে নিজেদের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতা এবং রাষ্ট্র-কর্তারুপে যুগপৎ মানিয়া লইলেন এবং তাঁহাদের আহ্বানে তিনি মদীনায় চলিয়া গেলেন। নবী করীম(স) হইলেন তাঁহাদের একচ্ছত্র নেতা।}নামে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। এই সময় দুইজন স্ত্রীলোকসহ মদিনার আওস ও খাজরাজ নামক দুই প্রধান বিবাদমান গোত্রের মোট প্রায় ৭৫জন মুসলমান ঐক্যবদ্ধ হইয়া রাসূলে করীম(স)-এর হাতে ‘বায়’আত’ গ্রহন করেন। এই বায়’আতে তাঁহারা দ্বীন- ইসলামকে পুর্নাঙ্গভাবে মানিয়া ও অনুসরণ করিয়া চলার সঙ্গে সঙ্গে নবী করীম(স)-এর সার্বিক নেতৃত্ব মানিয়া লওয়ার,তাঁহার জন্য পূর্ণ নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহন করার এবং তাঁহার নেতৃত্বে বিরুদ্ধ পক্ষের সহিত প্রাণ-পণ যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হওয়ার অঙ্গীকার দান করেন। শুধু তাহাই নয়, নবী করীম(স)-কে তাঁহার সঙ্গী-সাথীসহ মদীনায় যাইবার জন্য তাঁহারা আহ্বান জানান এবং সেখানে তাঁহাদিগকে বসবাসের জন্য স্থান দেওয়ার প্রতিশ্রুতিরও পুনরুল্লেখ করেন। মদীনাবাসীরা নবী করীম(স)-কে একজন ‘আশ্রয় গ্রহণকারী’(Settler-Asylum) রুপে নয়-আল্লাহ্র রাসূল ও প্রতিনিধি এবং তাঁহাদের সর্বাত্মক নেতা ও প্রশাসক হিসেবেই এই আহ্বান জানাইয়াছিলেন। নবী করীম(স) এই আহ্বান গ্রহন করিয়া সঙ্গিসাথী সমভিব্যহারে মদিনায় স্থানান্তরিত হওয়ার সিদ্ধান্ত ও এইখানে ঘোষণা করেন। বস্তুতঃ একটি রাষ্ট্রের দানা বাঁধিয়া উঠার মূলে সর্বপ্রথম যে সামাজিক-সামষ্ঠিক চুক্তি(Social Contract)-র অবস্থিতি প্রথম শর্ত, মদীনায় প্রতিনিধি স্থানীয় অধিবাসীদের নিকট হইতে নবী করীম(স)-এর গৃহীত আকাবার এই ‘বায়াআত’ সেই চুক্তিরই বাস্তব রূপ। প্রকৃতপক্ষে এই ‘বায়’আতে’র মাধ্যমেই ইসলামী রাষ্ট্রের প্রথম ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছিল। এই ‘বায়’আত’ মক্কার এক নির্জন পর্বতগুহায় অনুষ্ঠিত হইলেও উহার জন্য স্থান(Territory)নির্দিষ্ট হইয়াছিল মদীনা। ‘মদীনা’ এই সময় হইতেই ‘মদীনাতুর-রাসূল’- রাসূলের মদীনা কিংবা ‘মদীনাতুল-ইসলাম’- ইসলামের কেন্দ্রভূমি মদীনা-নামে অভিহিত হইতে শুরু করিয়াছিল।পাশ্চাত্য রাষ্ট্রবিজ্ঞানে একটি রাষ্ট্র(State)-এর সর্বশেষ সংজ্ঞায় যে কয়টি জরুরী শর্ত উল্লেখিত হইয়াছে,সেই সব কয়টিই এখানে পুরাপুরি বর্তমান মদিনার মুসলমানগণ যে ‘বায়আত’ করিয়াছিলেন এবং এই প্রসঙ্গে উভয় পক্ষে যে কথোপকথন হইয়াছিল, তাহা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, নবী করীম (স)-কে তাঁহারা মদীনা গমনের আহ্বান জানাইয়া এক কঠিন বিপদের ঝুঁকি মাথায় লইয়াছিলেন।তাঁহারা ইহা অবলীলাক্রমে সহ্য করিয়া যাইতে সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত ছিলেন। অন্যকথায়, একটি ক্ষুদ্রায়তন উপশহর যেন নিজেকে নিজে সমগ্র দেশের চূরান্ত শত্রুতা এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক বয়কটের মুখে ঠেলিয়া দিতেছিল। অবশ্য ইহার পরিনতিও ঠিক তাহাই হইয়াছিল।
অপরদিকে মক্কাবাসীদের জন্য ও এই বায়’আত বিশেষ অর্থবহ এবং বিপজ্জনক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। কেননা মুসলমানগণ মক্কার বাহিরে অন্য একস্থানে একত্রিত হইলেও- ইহারই মাধ্যমে একটি শক্তি, একটি রাষ্ট্ররূপে এবং মক্কাবাসীদের কুফর-শিরক, অরাজকতা-উচ্ছৃঙ্খলতার প্রতি একটা মারাত্মক চ্যালেঞ্জ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। অর্থাৎ মক্কাবাসীদের জন্য ইহা শুধু ধর্মীয় বিপদই নয়, ইহা একটি সুস্পষ্ট ‘রাজনৈতিক বিপদ’ হইয়া দেখা দিয়াছিল। মদিনা যেহেতু ইয়ামেন হইয়া সিরীয়া যাওয়ার বাণিজ্য পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান সেহেতু এখানে মুসলমানদের রাষ্ট্ররূপে পরিগ্রহের ফলে এই পথটি তাহাদের জন্য চিরতরে বন্ধ হইয়া যাইবার কিংবা অন্ততঃবিপদ-সঙ্কুল হইয়া পড়ার আশংকা দেখা দিয়াছিল। অথচ এই পথটি ছিল কুরাইশ ও অনন্যা বড় বড় গোত্রের লোকদের অর্থনৈতিক জীবনের প্রধান যোগসূত্র। কুরাইশরা ইহার পরিণতি মর্মে মর্মে অনুধাবন করিতে পারিয়াছিল। সে কারণে তাহারা বিশ্বনবীর জীবন-প্রদীপ চিরতরে নির্বাপিত করিয়া ফেলার জন্য পূর্বাহ্ণেই ঐক্যবদ্ধভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহন করিয়াছিল।
এক কথায়, এই ‘বায়’আত’ একদিকে যেমন ছিল প্রথম ইসলামী রাষ্ট্র-সংস্থার ভিত্তিপ্রস্তর, অপরদিকে ইহার মাধ্যমে একটি আদর্শিক সমাজ-সংস্থার ভিত্তিও সংস্থাপিত হইয়াছিল। বস্তুতঃ জানা ইতিহাসে(Known History) পুরাপুরি আদর্শ-ভিত্তিক রাষ্ট্র বলিতে এইটিকেই বুঝায়।
মদিনায় ইসলামী রাষ্ট্র
আকাবার বায়’আত অনুসারে রাসূলে করীম(স)-এর হিজরাতের সঙ্গে সঙ্গে ইসলাম মদীনায় স্থানান্তরিত হইল। প্রথমে যাহা ছিল বীজ, এক্ষণে তাহাই হইল বৃক্ষ। যাহা ছিল থিওরী(Theory),এক্ষণে তাহাই হইল বাস্তব(Practical)। প্রথম যাহা ছিল নিছক মৌখিক আনুগত্যর মধ্যে সীমাবদ্ধ, এক্ষণে তাহাই দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডে ও সামাজিক-সামষ্ঠিক বিষয়াদিতে অনুসৃত হইয়া শরীরী হইয়া উঠিল। মক্কায় যাহা ছিল সূচনা, মদীনায় তাহাই অগ্রগতির স্তরসমূহ অতিক্রম করিয়া ধাপে ধাপে পুর্নত্তের দিকে আগাইয়া যাইতে লাগিল।
মদীনায় পৌছিয়া নবী করীম(স) প্রথম পর্যায়েই দুইটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করিলেন। প্রথম কাজটি হইল, একটি মসজিদের ভিত্তিস্থাপন। এই মসজিদ কেবল পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ার স্থানই নয়, ইহা মুসলিম জনতার মিলন-কেন্দ্রে পরিণত হইল। এই স্থানকে কেন্দ্র করিয়াই নবী করীম(স) ইসলামের জন্য আত্মোৎসর্গীকৃত লোকদের লইয়া একটি আদর্শ-ভিত্তিক সামাজিক-সামষ্ঠিক শক্তির লালন ও বিকাশ সাধনের জন্য প্রচেষ্টা চালাইয়া যাইতে শুরু করিলেন। তিনি ইসলামের মহান আদর্শের ভিত্তিতে একটি পুর্নাঙ্গ রাষ্ট্র পরিচালনের যোগ্য নাগরিক ও কর্মী-নেতৃবাহিনী গড়িয়া তোলার সর্বাত্মক সাধনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন এই মসজিদকে কেন্দ্র করিয়া। এই মসজিদই ছিল রাষ্ট্রপ্রধান ভবন,সেনাধ্যক্ষর(Supreme Commander) হেড কোয়ার্টার এবং সর্বোচ্চ প্রশাসকের কেন্দ্রীয় অফিস।
দ্বিতীয় কাজ হইল, মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে পারস্পরিক ভ্রাতৃসম্পর্ক স্থাপন। ইহা ছিল কুরআনের সুস্পষ্ট নির্দেশের বাস্তব অনুসরণ। নির্দেশটি এইঃ
*******(আরবী)
মু’মিন লোকেরা পরস্পরের ভাই; অতএব তোমরা এই ভাইদের মধ্যে পারস্পরিক সন্ধি ও কল্যাণ স্থাপন কর। আর সকলে সম্মিলিতভাবে আল্লাহ্কে ভয় করিয়া চল; তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করা হইবে বলিয়া আশা করা যায়।
ইসলাম সমগ্র বিশমানবতার অভিন্ন ভ্রাতৃত্বের পয়গাম লইয়া আসা গতিশীল ও যুগোপযোগী এক মহান বিধান। বর্ণিত ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়া রাসূলে করীম(স) সেই বিরাট বিশ্বমানবিকতারই ভিত্তি স্থাপন ও কর্ম-ধারার সূচনা করিয়াছিলেন।ইহার মাধ্যমে তিনি স্থান-কাল-ভূগলের সীমা ও ভাষার পার্থক্য এবং বংশ-রক্ত-গোত্রের বিভেদ সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করিয়া দিলেন। এই ভ্রাতৃ-সম্পর্কের কারণে স্থানীয় ও অস্থানীয় ভেদাভেদো চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। সমস্ত বৈষয়িক-বস্তুগত পার্থক্য-বিভেদ নিঃশেষ করিয়া দিয়া নবী করীম (স) এক সার্বজনীন ভ্রাতৃত্বের সমাজ(Society of Universal Brotherhood) গড়িয়া তুলিতে শুরু করিয়াছিলেন।
এই ভ্রাতৃপ্রতীম সমাজের ভাবধারা ছিল এই যে, এখানে কেউ ছোট নয়, কেউ বড় নয়। কেউ হীন নয়, কেউ মানী হয়। কেউ আশরাফ নয়, কেউ আতরাফ নয়। কেউ কুলীন নয়, কেউ অকুলীন নয়। এই সমাজের প্রতিটি মানুষ ইসলামের মহান আদর্শে সমান মর্যাদা ও অধিকারসম্পন্ন ভাই মাত্র। ‘মুসলমান’ ই ইহাদের একমাত্র পরিচয়। ইহা ছাড়া তাহাদের আর কোন পরিচয় নাই।
দ্বিতীয় পর্যায়ে এই ভ্রাতৃত্ববোধক নবী করীম(স) সমাজ পুনর্গঠনের ও পুনর্বাসনের একটি কার্যকর হাতিয়ারে পরিণত করেন। তাহার গঠিত এই সমাজের প্রত্যেক ভাই তাহার অপর ভাইয়ের জন্য প্রয়োজনীয় সর্ব প্রকার ত্যাগ স্বীকার করিতে সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত। যাহার আছে সে সেই সব কিছুই দিবে তাহাকে,যাহার সেইসব নাই। কিন্তু ইহা ‘দান’ হইবেনা-হইবেনা ‘অনুগ্রহ’।গ্রহীতা তাহা গ্রহন করিয়া দাতার প্রতি হইবেনা অনুগ্রহীত,করুণার পাত্র-লাঞ্ছিত ও অবমানিত। ইহা তাহার কর্তব্য। একজন তাহার ভাইকে কিছু দিবে, দেওয়া তাহার কর্তব্য বলিয়া। ভাই তাহা গ্রহন করিবে তাহার ভাইয়ের কর্তব্য পালনে সহযোগিতা করার মানসিকতা লইয়া। ইহারই পরিণতিতে কল্পনাতীত স্বল্প সময়ে মক্কা হইতে নিঃস্ব সর্বস্বান্ত হইয়া আসা বিপুল সংখ্যক লোকের পুনর্বাসনের কঠিন ও জটিল সমস্যার অনায়াসে সমাধান হইয়াছিল। শুধু তাহাই নয়, সামগ্রিকভাবে নব প্রতিষ্ঠিত ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র বিপুল সচ্ছলতায় সমৃদ্ধ এবং নূতন শক্তিতে বলিয়ান হইয়া উঠিয়াছিল। প্রতিটি নাগরিকই নিজের উপার্জনের প্রেরণা ও সুযোগ লাভ করিল। ফলে কেহ কাহারও উপর ‘বোঝা’ বা নির্ভরশীল(Dependent) হইয়া থাকিল না।
তৃতীয় পর্যায়ে বিশ্লিষ্টটা ও বিশৃঙ্খলার বুক হইতে ঐক্য, সংহতি ও শৃঙ্খলা গড়িয়া তোলার কঠিন দায়িত্ব রাসূলে করীম (স)-এর সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিল। কার্যতঃ ইহা ছিল একটা পর্বততুল্য বিরাট সমস্যা। অতিতের নবি-রাসূলগণ ও এই সমস্যাটির সমাধানে সফল হইতে পারেন নাই। কিন্তু রাসূলে করীম(স)-কে তাহাই করিতে হইয়াছে এবং তিনি তাহা করিয়াছেন অপূর্ব সাফল্য ও যোগ্যতা সহকারে। দৌর্বল্য,অক্ষমতা ও শক্তিহীনতা বুক দীর্ণ করিয়া শক্তি ও সামর্থের বিরাট বৃক্ষ গড়িয়া তোলাই ছিল তাঁহার সাধনা। পারস্পরিক বিরোধ ও বৈষম্য দূরীভূত করিয়া নিঃছিদ্র একত্বটা ও ঐক্যবদ্ধটা সৃষ্টি করাই ছিল তাঁহার লক্ষ্য। মৃত্যুর তুহীন হিম অপসারিত করিয়া জীবনের উষ্ণতা,চাঞ্চল্য ও তৎপরতা নূতন জগত নির্মাণই ছিল তাহার কর্তব্য। আল্লাহ্ তা’য়ালা এই দিকে ইংগিত করিয়াই বলিয়াছেনঃ
********(আরবী)
এবং আমরা আপনার সেই দুর্বহ বোঝাটি আপনার উপর হইতে নামাইয়া দিলাম,যাহা আপনার পৃষ্ঠদেশ নিচু করিয়া দিয়াছিল।
চতুর্থ পর্যায়ে তাঁহার কর্তব্য ছিল ‘বাহির সামলানো’। এ পর্যন্ত তিনি যাহা কিছু করিয়াছেন তাহাকে বলা চলে ঘর সামলানোর কাজ। কিন্তু কেবল ঘর সামলাইলেই দায়িত্ব পালন সম্পূর্ণ হয় না।ইসলামী সমাজের আভ্যন্তরীণ ঐক্য ও নিরাপত্তা বিধানের পর উহাকে স্থায়ীভাবে সংরক্ষিত করার জন্য দুই পর্যায়ের কাজ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিল। একটি ছিল,ঘরের সংলগ্ন পরিমণ্ডলে অবস্থানকারী অমুসলিম ইয়াহুদি সমাজের নিত্য-নৈমিত্তিক-তথা প্রতি মুহূর্তের শত্রুতার আক্রমন হইতে ইসলামী সমাজের নিরাপত্তা বিধান। আর দ্বিতীয় কাজটি হইল, বহিঃশত্রুর সর্বাত্মক আক্রমণ হইতে ইসলামী রাষ্ট্রের এই নব নির্মিত প্রাসাদটির পুর্নাঙ্গ সংস্করণের সুষ্ঠু ও নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহন আর সেই সঙ্গে সমগ্র বিশ্বে ইসলামের ব্যাপক প্রচারের রাজপথ উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া।
তখনকার মদীনা শহরে এক প্রকার নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা অবস্থা বিরাজ করিতেছিল।সেখানকার আওস ও খাজরাজ এই দুইটি বড় ও প্রধান গোত্র প্রায় চারটি খণ্ডে বিভক্ত ছিল। অপর দিকে ইয়াহুদিদের দশটি গোত্র ছিল তাহাদের হইতে স্বতন্ত্র। শতশত বৎসরের শত্রুতা তাহাদিগকে পরস্পরের প্রানের দুশমন বানাইয়া দিয়াছিল।সাধারনতঃ কয়েকটি আরব গোত্র তাহাদের শত্রুদের সঙ্গে লড়াই করার উদ্দেশ্য ইয়াহুদিদের সহায়তা আদায় করিয়া লইত। অপর কতিপয় আরব গোত্র অন্য কয়েকটি বিরোধী গোত্রের সাহায্য লাভ করিত। অতঃপর যে রক্তাক্ত যুদ্ধ শুরু হইয়া যাইত,তাহা বংশানুক্রমে ও শতাব্দীকাল ধরিয়া অব্যাহত থাকিত। ইহার ফলে আরবের সাধারণ মানুষের জীবনে চরম দুঃখ ও কষ্ট নামিয়া আসিত। তাহারা এই প্রাণান্তকর অবস্থা হইতে মুক্তি লাভের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা চালাইতেছিল। এই জন্য নবী করীম(স)-এর মদীনা আগমনের প্রাক্কালে মদীনাবাসীদের একটা বিরাট অংশ আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সলুলকে নিজেদের বাদশাহ ও শাসক নিযুক্ত করার সিদ্ধান্ত লইয়াছিল। নবী করীম(স) মদীনার জনগনের এই অবস্থা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। এই অবস্থার পরিবর্তনের জন্য তিনি আকাবা বায়আত গ্রহনের পরই মদীনার বিভিন্ন গোত্রের বারো জন সদস্যকে ‘নকীব’ নিযুক্ত করিয়াছিলেন এবং এইভাবে তিনি পারস্পরিক সংঘর্ষলিপ্ত ও বিবাদমান গোত্রগুলির মধ্যে একটা মিলমিশ ও ঐক্য সৃষ্টির জন্য চেষ্টা চালাইয়াছিলেন। কিন্তু এই গোত্রবাদী সমাজের প্রতিটি গোত্রই ছিল সম্পূর্ণ স্বাধীন,স্ব-ব্যবস্থাপনার(Self-administration) অধিকারী এবং নিজেদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বেচ্ছানুবর্তী।এতদ্ব্যতীত সেখানে এই গোত্রসমূহকে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত ও ঐক্যবদ্ধ রাখিবার কোন প্রশাসন-ব্যবস্থা বা কার্যকর প্রতিষ্ঠান(Executive Institution)-ই ছিলনা। এতৎসত্ত্বেও নবী করীম(স) প্রেরিত ইসলাম প্রচারকদের চেষ্টায় মদীনাবাসীদের মধ্য হইতে বহু সংখ্যক লোক ইসলাম গ্রহন করিয়া মুসলিম সমাজের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল,যদিও তখন পর্যন্ত মদীনায় ইসলাম কোন রাজনৈতিক শক্তির মর্যাদা লাভ করিতে পারে নাই।
নবী করীম (স) মদীনায় উপস্থিত হইয়া এই অরাজক পরিস্থিতির অবসান ঘটাইবার উদ্দেশ্য একটি ঘোষণাপত্র তৈয়ার করিলেন।১ {ইতিহাসে এই ঘোষণাই ‘মদিনা-সনদ’ নামে বিধৃত।} এই ঘোষণায় মদীনা একটি ‘নগর রাষ্ট্রের’(city state) মর্যাদা পাইল। উহার ভিত্তিতে সমগ্র বিচ্ছিন্ন দো বিক্ষিপ্ত গোত্রসমূহের মধ্যে বিশেষভাবে ঐক্য ও সংহতি সৃষ্টির জন্য যারপরনাই চেষ্টা করা হইল।
একথা সর্বজনবিদিত যে, এই লোকেরা অতিতে কখনই কোন রাষ্ট্রশক্তির(State-power/coercive power)নিকট মাথা নত করে নাই। কোন দিনই তাহারা কেন্দ্রীয় শক্তির নিয়ম-শৃঙ্খলা ও প্রভুত্বের অধীনতা পাশে আবদ্ধ ছিল না। নবী করীম(স) এই ঘোষণাপত্রের সাহায্যে তাহাদের সকলকে একটি আইন, তথা এক আল্লাহ্, এক নেতৃত্ব ও একই কিবলার উপর সুসংবদ্ধ ও সুসংহত করিয়া দিলেন। ব্যক্তিগত অধিকারের দিক দিয়া মদীনা-ঘোষণা(Medina Diclaration) ছিল একটি বিপ্লবাত্মক পদক্ষেপ। পূর্বে যে অধিকার এক ব্যক্তি বা একটি পরিবার কিংবা একটি গোত্র ভোগ করিত, এই ঘোষণা কার্যকর হওয়ার পর তাহা সর্বসাধারণের অধিকার রূপে সাব্যস্ত হইল। এইভাবে একদিকে গোত্রবাদমূলক নৈরাজ্যের অবসান ঘটিল এবং অপরদিকে সঠিক অর্থে ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপিত হইল।
মদীনা-চুক্তি(Medina Pact)-র ধারা অনুযায়ী সমগ্র প্রশাসনিক(Administrative),আইনগত(Legal)ও ফৌজদারি বা বিচার বিভাগীয়(Judicial) ক্ষমতা হযরত মুহাম্মাদ(স)-এর উপর অর্পিত হইয়াছিল। তবে এই ব্যাপারে বিশ্বনবী ও দুনিয়ার অন্যান্য শাসকদের মধ্যে বিরাট পার্থক্য বিদ্যমান। তিনি কোন স্বেচ্ছাচারী ও দুর্বিনীত শাসক রূপে এই ব্যাপক ও সর্বময় ক্ষমতা গ্রহন করেন নাই। কোনরূপে ব্যক্তি স্বার্থ,ব্যক্তি সার্বভৌমত্ব ও ব্যক্তি আধিপত্যের একবিন্দু ধারণাও তাঁহার সম্পর্কে করা যাইতে পারেনা;বরং তাঁহার রাষ্ট্রনীতি উন্নত নৈতিক ও মানবিক আদর্শের উপর ভিত্তিশীল ছিল। তিনি নিজেকে একজন সার্বভৌম(Sovereign) হিসাবে এক মুহূর্তের তরেও চিন্তা করেন নাই, জনসমক্ষে সেভাবে নিজেকে পেশও করেন নাই। যে আইন তিনি অন্যদের উপর প্রয়োগ করিতেন, তাহা অন্যদের ন্যায় নিজের উপরও প্রয়োগযোগ্য মনে করিতেন। বস্তুত দুনিয়ার রাষ্ট্রীয় ইতিহাসে ইহার কোন দৃষ্টান্ত দেখানো যাইতে পারে না।
মদীনা-চুক্তি দুইটি অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশ ২৩টি ধারা সমন্বিত।উহা সম্পূর্ণ মুহাজির ও আনসারদের সহিত সংশ্লিষ্ট। আর দ্বিতীয় অংশ মদীনার ইয়াহুদীদের অধিকার ও কর্তব্য-দায়িত্ব সম্পর্কিত।
এই চুক্তি অনুযায়ী সমাজ ও রাষ্ট্রের সর্ব ব্যাপারে নবী করিম (স)-এর ফয়সালা ও রায়ই ছিল চূরান্ত। বিচার বিভাগীয় সর্বোচ্চ মর্যাদা ও ছিল তাহাঁরই। মুহাজির ও আনসার জনগণ তো দ্বীন-ইসলাম কবুল করার সঙ্গে সঙ্গে রাসূলে করীম(স)-কে শুধু ধর্মীয় নেতাই নয়- সমাজ-রাষ্ট্রকর্তা হিসাবেও সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী রূপে স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। কজেই এই ধরনের চুক্তিতে তাহাদের কোনরূপ আপত্তি থাকার প্রশ্নই উঠিতে পারে না। কিন্তু ইয়াহুদী সমাজ তো সমগ্র আরবের উপরই নিজেদের সাংস্কৃতিক প্রাধান্যের দাবিদার ছিল। এতৎসত্ত্বেও তাহাদের পক্ষে এইরুপ ধারা সমন্বিত চুক্তিতে সম্মত হওয়া ছিল বিশ্বনবীর রাষ্ট্রনীতির একটা বিরাট মুজিজা।
মদীনা-চুক্তির উল্লেখযোগ্য ধারাসমূহ
মদীনা-চুক্তির ধারাসমূহ বিস্তারিতভাবে উদ্ধৃত করা এখানে সম্ভবপর নয়। সংক্ষেপে উহার গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি ধারা এবং তৎসংক্রান্ত সাধারণ পর্যালোচনা এখানে পেশ করা যাইতেছে।
ঘোষণাপত্রের প্রথম অংশ হইতে যে রাষ্ট্ররূপ দানা বাঁধিয়া উঠে,তাহা মুহাজির,আনসার ও সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ অন্যান্য গোত্র এবং লোকদের সমন্বয়ে গঠিত। এই সমস্ত লোক সুস্পষ্ট ভাষায় নবী করীম(স)-এর নেতৃত্বে মানিয়া চলার ও তাঁহার সহিত একত্রিত হইয়া শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য অঙ্গিকারবদ্ধ হইয়াছিল। নিজেদের মধ্যে শতধা-বিভক্তি ও বিভেদ থাকা সত্ত্বেও ইহারা সমগ্র বিশ্বসমাজ হইতে স্বতন্ত্র একটি একক(Unit)গড়িয়া তুলিয়াছিল।গোটা মুসলিম জনতা অধিকার ও কর্তব্যে সম্পূর্ণ অভিন্ন মর্যাদা গ্রহন করিয়াছিল। যুদ্ধ ও সন্ধি রাষ্ট্রীয় ও সামষ্ঠিক বিশয় রূপে গণ্য হইল। সামরিক দায়িত্ব সকলের জন্য অবশ্যই পালনীয় হইল। নিরাপত্তার অঙ্গীকার দেওয়ার অধিকার প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য নির্দিষ্ট হইল।চুক্তিবদ্ধ হওয়ার অধিকার প্রত্যেকের এবং একজনের চুক্তি সকলের জন্য বাধ্যতামূলক হইয়া গেল। ইহার ফলে রাষ্ট্রীয় সংস্থায় পূর্ণ ভ্রাতৃত্ব,সাম্য ও ব্যক্তি-স্বাধীনতার এক স্বর্ণযুগ সূচীত হইল।
এই চুক্তি অনুযায়ী মক্কার কুরাইশ পক্ষাবলম্বনে বা তাহাদের কোনরূপ সাহায্য ও আশ্রয়দানের অধিকার কাহার ও থাকিল না। উপরন্তু কুরাইশদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের অগ্রাভিযানে কোন রূপ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি কিংবা বিরুদ্ধতা করাও কাহারও পক্ষে সম্ভব থাকিল না।
সমস্ত ব্যাপারে সর্বোচ্চ ও সর্বশেষ আদালতের মর্যাদা পাইলেন স্বয়ং হযরত মুহাম্মাদ(স)।
অতঃপর আদালতী ব্যবস্থা আর এক ব্যক্তি বা একটি গোত্রের ব্যাপার হইয়া থাকিল না,বরং ইহা একটি সামষ্ঠিক ও সামাজিক মর্যাদা লাভ করিল।গোটা বিচার বিভাগীয় ক্ষমতাই কেন্দ্রীয় মর্যাদা পাইল।ইহাও ছিল একটি বিপ্লবাত্মক সিদ্ধান্ত।এই সিদ্ধান্তের ফলে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতা ও অবিমিশ্র সুবিচার সর্বত্র প্রাধান্য লাভ করিল।কোনরূপ পক্ষপাতিত্ব কিংবা স্বজন-প্রীতি বা আত্মীয়-প্রীতির সামান্য পথ ও উন্মুক্ত থাকিল না। সমস্ত মুসলমান সামগ্রিকভাবে এই জন্য দায়ী হইল যে, কেহ কাহারও উপর অত্যাচার করিতে পারিবেনা;কেহ কাহারও অধিকার হরণ করিতে পারিবেনা।
মদীনা-চুক্তির দ্বিতীয় অংশ সম্পূর্ণরূপে ইয়াহুদীদের সহিত সম্পর্কিত ছিল।সমস্ত ইয়াহুদী জনগোষ্ঠী একটি সমষ্ঠি হিসাবে ফেডারেল পদ্ধতির ‘মদীনা নগর- রাস্ত্রের’সহিত যুক্ত হইয়াছিল।প্রথম ধারাটিতে বলা হইয়াছিল যে,ইয়াহুদী ও মুসলমানরা যুক্তভাবে যদি কোন যুদ্ধ করে, তাহা হইলে প্রত্যেকেই নিজের নিজের ব্যয়ভার বহন করিবে। উভয়ই নিজেদের ধর্ম পালনে পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করবে। এভাবে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ব্যাপারে ইয়াহুদীরা মুসলমানদের সমান অধিকার লাভ করিল। দেশ রক্ষার দায়িত্বে ইহারা পরস্পরের সাহায্যকারী হইল। অর্থাৎ মুসলমান যাহাদের বিরুদ্ধে লড়াই করিবে,ইয়াহুদীরাও তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে বাধ্য হইবে। মুসলমানরা যাহাদের সহিত সন্ধি করিবে,ইয়াহুদীরাও তাহাদের সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হইবে। এই সময় দেশরক্ষার-অর্থাৎ মদীনা নগর-রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষার ব্যাপারে পরস্পরের কার্যকর সাহায্য করাও উভয়ের কর্তব্য হইবে। এই ধরনের চুক্তির ফলে প্রতিরক্ষা (Defense) ব্যাপারটিও কেন্দ্রীয় বিষয়ে গণ্য হইল।অতঃপর রাসূলে করীম(স)মুসলিম ও ইয়াহুদী সমন্বয়ে গঠিত সম্মিলিত সেনাবাহিনীর প্রধান (Head and supreme) হইলেন। ইহাই রাসূলে করীম(স)-এর আর একটি বিরাট রাজনৈতিক সাফল্য।
রাসূলে করীম(স)ইয়াহুদিদের একান্ত আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কিছুমাত্র হস্তক্ষেপ করিতেননা।ইহার ফলে তাহাদের মনে যে বিদ্বেষ ও আশঙ্কার কালোমেঘ পুঞ্জিভূত হইয়াছিল,তাহা অতি সহজেই বিলীন হইয়া গেল। তাহারা নিজেরাই সোৎসাহে নিজেদের যাবতীয় ব্যাপারে রাসূলে করীম(স)-কেই সর্বোচ্চ বিচারক হিসাবে মানিয়া ইয়াছিল।আত্মীয়তার ভিত্তিতে তাহাতে কোনরূপ প্রভাব বিস্তার করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হইয়া গেল। এইভাবে জাহিলিয়াত যুগের সমস্ত বাতিল নীতির নিদর্শনাদি নিঃশেষে মুছিয়া ফেলা হইল। অবস্থা এই দাঁড়াইল যে,ইয়াহুদীরা নবী করীম(স)-কে শুধু নিজেদের প্রশাসক মানিয়াই ক্ষান্ত হইল না, সমস্ত মদীনাকে তাহারা একটি ‘হারাম’(সুরক্ষিত ও সংরক্ষিত এলাকা)ও বানাইয়া লইল।ইহাও রাসূলে করীম(স)-এর রাষ্ট্রনৈতিক প্রজ্ঞা ও ধীশক্তির একটা বিরাট পরাকাষ্ঠা ছিল।( পরবর্তী সময়ে অবশ্য ইয়াহুদিরা প্রকাশ্যে রাষ্ট্রবিরোধী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হওয়ার দরুণ মদীনা হইতে শেষ পর্যন্ত নির্বাসিত হইতে বাধ্য হইয়াছিল।)
মদিনা নগর-রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা ও উহার সংরক্ষণ ব্যবস্থার জন্য আভ্যন্তরীণ দৃঢ়তা বিধানের সঙ্গে সঙ্গে নগরীর উপকণ্ঠে বসবাসকারী গোত্রসমূহের সহিত মিত্রতার সম্পর্ক গড়িয়া তোলাও অপরিহার্য ছিল। এই উদ্দেশ্যে নবী করীম(স) পশ্চিম অঞ্চল ও সীমান্তবর্তী জিলাসমূহ পরিভ্রমণ ও পরিদর্শন করিয়া সেখানকার গোত্রসমূহের সহিত বেশ কয়েকটি চুক্তি স্বাক্ষর করনে। ফলে এইসব গোত্র মুসলমানদের সহিত প্রতিরক্ষার ব্যাপারে মিত্র শক্তি হইয়া দাঁড়াইল।অতঃপর মদীনার চতুর্দিকের গোত্রগুলি মুসলমানদের সহিত শত্রুতা করার পরিবর্তে বিশেষ সাহায্যকারী হইয়া উঠিল।
চূড়ান্ত পদক্ষেপ
মদীনার আভ্যন্তরীণ ও পারিপার্শ্বিক দিক দিয়া পূর্ণ নিরাপত্তা ও নিশ্চিন্ততা লাভ করার পর নবী করীম(স) মক্কার কুরাইশদের সহিত দশ বছরের জন্য সন্ধি-চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এই চুক্তি “হুদাইবিয়া’ নামক স্থানে সম্পাদিত হওয়ায় ইতিহাসে ইহা ‘হুদাইবিয়া সন্ধি’ নামে পরিচিত।এই চুক্তি প্রকৃতপক্ষে মুসলমানদের জন্য ‘ফতহুম-মুবীন’-‘সুস্পষ্ট ও সমুদ্ভাসিত বিজয়’-নামে আল্লাহ্র কালাম কুরআন মজীদেই অভিহিত হইয়াছে। এই সন্ধি-চুক্তি সাক্ষরিত হওয়ার পর নবী করীম(স) সমগ্র আরব দেশে ব্যাপক ও সর্বাত্মকভাবে ইসলাম প্রচারের অবাধ ও নির্বিঘ্ন সুযোগ লাভ করিলেন। সেই সঙ্গে ইয়াহুদীদের শক্তি কেন্দ্র খায়বর হইতেও তাহাদিগকে চিরতরে ও সমূলে উচ্ছেদ করার উপায় হইয়া গেল।খায়বরের দুর্ভেদ্য দুর্গপ্রাকার জয় করার পর নবী করীম(স) সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ ও রক্তপাতহীন নিয়মে মক্কা শরীফ জয় করিতে সমর্থ হইলেন। অষ্টম হিজরী সনে মক্কা বিজয়ের পর নবী করীম(স) সমগ্র আরব উপদ্বীপটিকে ইসলামের একক ও নিরংকুশ শাসনাধীনে ঐক্যবদ্ধ করিয়া লইতে সমর্থ হইলেন। এইভাবে তিনি নিজের জীবনেই ইসলামী রাষ্ট্রকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর সংস্থাপিত করিয়া দিয়াছিলে।
বলা বাহুল্য,রাসূলে করীম(স) প্রতিষ্ঠিত এই রাষ্ট্রটি নিছক একটি রাষ্ট্রমাত্র ছিল না। ইহা ছিল বাস্তবে অস্তিত্বহীন একটি আদর্শবাদের পূর্নাঙ্গ বাস্তবায়ন।যে বীজটি আরব ভূ-খন্ডেরই একটি নির্জন স্থানে অতিশয় গোপনে উপ্ত হইয়াছিল একুশ বৎসর পূর্বে, উত্তরকালে তাহাই এক বিরাট মহীরুপে পরিণত হইয়া সমগ্র আরব দেশকে নিজের সুশীতল ছায়াতলে আনিয়া বিশ্বমানবতার জন্য চিরস্থায়ী এক আলোক কেন্দ্র(Light House)স্থাপন করিয়া দিয়াছিল। অনন্তকাল পর্যন্ত দুনিয়ার মানুষের জীবনে এই আলক-কেন্দ্র হইতে অজস্র ধারায় আলোকচ্ছটা বিচ্চুরিত হইতে থাকিবে এবং অত্যাচার-নিপীড়নে জর্জরিত দিশাহারা মানুষ উহা হইতেই মুক্তি ও কল্যাণ পথের নির্ভুল সন্ধান লাভ করিতে থাকিবে।
নবী-প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য
এইখানে নবী করীম(স) প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র ব্যবস্থার বিশেষত্ব ও বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা আবশ্যক। সংক্ষেপে তাহাই পেশ করা যাইতেছে।
(১)নবী-প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র সামাজিক-সামষ্ঠিক চুক্তি ও প্রতিশ্রুতির(Social Contract)ভিত্তিতে গড়িয়া উথা পৃথিবীর সর্বপ্রথম রাষ্ট্র ব্যবস্থা। মানব ইতিহাসে এই ধরনের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কোন দৃষ্টান্ত খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। নবুয়্যাতের ত্রয়োদশ বৎসর মদীনার লোকেরা স্বেচ্ছায় ও সাগ্রহে নবী করীম(স)-এর হাতে যে ‘বায়’আত’ করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে নিজেদের ধর্মীয় নেতার সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক নেতা ও শাসকও মানিয়া লইয়াছিলেন, উত্তরকালে তাহাই পূর্ণ পরিণতি লাভ করিয়াছিল একটি পূর্নাঙ্গ সর্বাত্মক রাষ্ট্র ব্যবস্থায়।
(২)এই রাষ্ট্র ব্যবস্থার সার্বভৌমত্বের(Sovereignty) উৎস ছিল মহান আল্লাহ্র সত্তা-সম্পূর্ণ নিরক্কুশভাবে।সার্বভৌমত্ব বলিতে যাহা বুঝায়,তাহাতে অন্য কাহারও-স্বয়ং নবী করীম(স)-এর কোন অংশ ছিল না। হযরত মুহাম্মাদ(স) আল্লাহ্র রাসূল হিসাবে কুরআনী বিধানের ভিত্তিতে আইন প্রবর্তন ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করিতেন।সার্বভৌমত্বের এই প্রশ্নটিই ইসলামী রাষ্ট্র ও দুনিয়ার অন্যান্য রাষ্ট্র দর্শনের মাঝে আকাশ-পাতাল পার্থক্যের ভিত্তিপ্রস্তর। রাসূলে করীম(স) আল্লাহ্র নিকট হইতে ‘অহী’পাইতেন। সেই অহীই ছিল আইনের মূল সূত্র।কিন্তু সার্বভৌমত্বের অধিকার হিসাবে তিনি নিজেকে কস্মিনকালেও পেশ করেন নাই।‘অহীর’ ব্যাখ্যা তিনিই প্রদান করিতেন। কিন্তু উহার বাস্তবায়নে নিজেকে কখনো বাদ(Exempted)দেন নাই। বরঞ্ছ অহীর মাধ্যমে তাঁহার নিজের কাজের ‘ত্রুটি’ও জনগনের সম্মুখে উদঘাটিত হইয়াছে। তিনি নিজেই নিজের ‘অপরাধ’ বিচারের জন্য লোকদের নিকট নিজেকে বারবার পেশ করিয়াছে। ইহার ফলে ‘বাদশাহ’কে বা ‘সর্বোচ্চ প্রশাসক’কে আল্লাহ্র আসনে বসাইবার সকল ধারণা ও নীতিমালা(‘বাদশাহ কখনও ভুল করিতে পারেন না’-বাদশাহকে কখনও অভিযুক্ত করা যাইতে পারে না ইত্যাদি)সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা প্রমাণিত হইয়া গেল। ইহাতে এই সত্যও প্রতিষ্ঠিত হইল যে,আল্লাহ্র নিরংকুশ সার্বভৌমত্বের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রে কোন ব্যক্তি ‘বাদশাহ’ বা স্বৈরতন্ত্রী হইতে পারে না। কোন দল বা গোষ্ঠীর পক্ষেও তাহা সম্ভব নয়। মানুষকে গোলাম বানাইবার অধিকার কাহারও থাকিতে পারে না।
(৩) ইহা একটি পুর্নাঙ্গ আদর্শভিত্তিক রাষ্ট্র(Ideological State)।নবী করীম(স)-ই ইতিহাসে সর্বপ্রথম লিখিত শাসনতন্ত্রের(Written Constitution) ভিত্তিতে রাষ্ট্র পরিচালনা শুরু করেন। ইহা বংশ, দেশমাতৃকা,বর্ণ,ভাষা ও নিছক অর্থনৈতিক একাত্নতা-ভিত্তিক রাষ্ট্র ছিল না। ইহা ছিল ইসলামী জীবনাদর্শের ধারক ও বাহক জাতিধর্ম নির্বিশেষে গোটা বিশ্ব মানবতাকে ইসলামের প্রতি আহ্বানকারী প্রথম রাষ্ট্র। ইসলামী আদর্শের পূর্ণ বাস্তবায়ন ও উহার সর্বাত্মক বিজয় অর্জন এবং ইহার মাধ্যমে জনগনের সার্বিক কল্যাণ বিধানই এই রাষ্ট্রের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল।
উল্লেখ্য যে, ইসলামী রাষ্ট্র পাশ্চাত্ত্যের ফ্যাসিবাদী বা তথাকথিত গণতন্ত্রবাদী রাষ্ট্রের মত স্বতঃই কোন লক্ষ্য নয়-অর্থাৎ রাষ্ট্রের জন্য রাষ্ট্র নয়;বরং একটি আদর্শ বাস্তবায়নের মাধ্যমে একটি উন্নততর ও মহত্তর লক্ষ্য অর্জনই ইহার উদ্দেশ্য। আর তাহা হইল আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের পরিপূর্ণ আনুগত্য এবং আল্লাহ্র পরম সন্তুষ্টি অর্জন।একটি ধর্মহীন(Secular) গণতান্ত্রিক বা জাতীয় রাষ্ট্র কোন উচ্চতর নৈতিক বিধানের অনুগত হয় না। কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্র হয় উহার সম্পূর্ণ বিপরীত। ইহাতে ধর্মীয় ও বৈজ্ঞানিক যাবতীয় ব্যাপার আল্লাহ্র বিধানের ভিত্তিতে সুসম্পুন্ন হইয়া থাকে।
(৪) ইসলামে ধর্ম ও রাষ্ট্র একই জিনিসের পার্থক্যহীন দুইটি দিক মাত্র। পার্থক্য শুধু শব্দের,মূল জিনিসের বা ভাবধারা দিক দিয়া ইহাতে কোন পার্থক্য নাই।এখানে যাহা ধরম,তাহাই রাজনীতি আর যাহা রাজনীতি,তাহাতেই ধর্ম নিহিত। ইসলাম স্বতঃই এক পুর্নাঙ্গ দ্বীন। মানব জীবন ও বিশ্ব-প্রকৃতির এমন কোন দিক নাই, যে বিষয়ে ইসলামের বিধান অনুপস্থিত। রাসূলে করীম(স) একই সঙ্গে আল্লাহ্র প্রতিনিধি হিসাবে জীবনের সর্বদিকে ও সর্বক্ষেত্রে অবিসংবাদিত নেতা। জীবনের বিভিন্নতা ও দ্বৈততা ইসলামের পরিপন্থী। বস্তুতঃরাষ্ট্রীয় ধর্মহীনতা বা ধর্মনিরপেক্ষতা উনবিংশ শতকের পোপতন্ত্রের প্রতিক্রিয়ার ফসল। বর্তমানে ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে ইহা সম্পূর্ণরূপে অতীত।ইহার ভিত্তিতে কোন রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বর্তমানে যুগে অসম্ভব। কেননা সংশয়বাদ,মানসিক অস্থিরতা ও স্বার্থবাদ(Utilitarianism) ছাড়া উহা বিশ্বমানবতার জন্য অন্য কোন অবদানই রাখিতে পারে নাই।
(৫) ইসলামী রাষ্ট্র প্রকৃত অর্থেই একটি গণ-অধিকারসম্পন্ন এবং জনমত ভিত্তিক কার্যকর রাষ্ট্র ব্যবস্থা।এখানে সমস্ত রাষ্ট্রীয় ব্যাপার জনগণের সমর্থন ও অনুমোদনের ভিতিতেই সুসম্পন্ন হইয়া থাকে বলিয়া রাষ্ট্রীয় মৌল নীতির বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলদের সাথে পরামর্শ ভিন্ন কার্যকর হইতে পারে না। এই নীতি রাসূলে করীম(স) কর্তৃক পুরাপুরি অনুসৃত।
ব্যক্তি স্বাধীনতা, সাম্য ও সুবিচার গণ- অধিকারসম্পন্ন রাষ্ট্র ব্যবস্থার ভিত্তি বিশেষ।এইগুলির যথাযথ বাস্তবায়ন ব্যতিত গণ-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবতা ধারণাতীত। রাসূলে করীম(স) প্রতিষ্ঠিত প্রথম ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থাই সর্বপ্রথম মানুষের প্রকৃত আজাদী কার্যকর হয়। ইসলামের কালেমা ‘লা-ইলাহা ইল্লালাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ’ ঘোষণায়ই ব্যক্তি-স্বাধীনতার বিপ্লবী ভাবধারা এক অপূর্ব চেতনায় বিধৃত। এক আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাহারোই –কোন-কিছুরই-একবিন্দু গোলামী করিতে প্রস্তুত না থাকার ইহা এক বিপ্লবাত্মক ঘোষণা ছাড়া আর কিছুই নয়।
আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমার মধ্যে মানুষ ইসলামী রাষ্ট্রে সম্পূর্ণ আজাদ ও স্বাধীন।এখানে প্রত্যেকরই অধিকার সুনির্দিষ্ট।কোন অবস্থায়ই কাহারও অধিকার হরণ করার কাহারও অধিকার নাই। ইসলামের সোনালি যুগে কোন ব্যক্তিকে কোন অবস্থায়ই তাঁহার মৌলিক অধিকার হইতে বঞ্ছিত করা হইত না। কাহারও ব্যক্তিগত মত প্রকাশ ও প্রচার, পেশা-গ্রহন,সভা-সম্মেলন অনুষ্ঠান বা যত্রতন্ত্র যাতায়াতে শরীয়াত-ভিত্তিক কোন কারণ ছাড়া কখনও কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা বা বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হইত না। কেননা এইরুপ করা ইসলামের দৃষ্টিতে সুস্পষ্ট জুলুম ছাড়া আর কিছুই নয়। এই কারণেই রাষ্ট্রপ্রধান রাসূলে করীম(স)-র সহিত মতবিরোধ করিয়া ভিন্নতর মত প্রকাশ করার অধিকারও প্রত্যেকেরই ব্যক্তিই পাইয়াছে।
এই রাষ্ট্রের সাম্য ও সততা দুইটি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। একটি আদম সন্তান হওয়া-ইহার কারণে সমস্ত মানুষই মূলগতভাবে সমান। আর দ্বিতীয় ভিত্তি ভ্রাতৃত্ব। সমস্ত মুসলমান পরস্পরের ভাই এবং সর্বতোভাবে অভিন্ন।
সুবিচার এই রাষ্ট্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। সমদৃষ্টি ও নিরপেক্ষতা এই রাষ্ট্রের স্থায়ী নীতি।নবী করীম(স) নিজে সবসময় সুবিচার নীতিকে ভিত্তি করিয়াই ফয়সালা করিতেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রে আইনের প্রয়োগ ছিল নির্বিশেষ।এমন কি,একটি বিচার কার্যের সময় ‘ফাতিমা চুরি করিলে উহার দণ্ডস্বরূপ তাঁহারও হাত কাটা যাইবে’ বলিয়া ঘোষণা করিয়া তিনি বিচার ও আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে সমস্ত দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির মূলোৎপাটন করিয়া দিয়াছেন।
(৬)ইসলামী রাষ্ট্র সঠিক অর্থে একটি জনসেবক ও জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র (Welfare State)ছিল। রাসূলে করীম(স) প্রতিষ্ঠিত এই রাষ্ট্রে জনগনের কেবল আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতাই করা হইত না,ইতিবাচকভাবে গন-অধিকার আদায় করা ও জনগনের দারিদ্র্য নির্মূল করার জন্যও চেষ্টা চালান হইত।পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের মত ‘অর্থোপার্জনের প্রতিযোগিতায় পরাজিত’দের সম্পূর্ণ অসহায় করিয়া রাখা এই রাষ্ট্রে মোটেই সম্ভবপর ছিল না। সকল লোকের সম্মুখে অর্থনৈতিক সুজগ-সুবিধার দ্বার সমানভাবে উন্মুক্ত করিয়া দেওয়ার পরও পিছনে পড়িয়া থাকা লোকদের আর্থিক নিরাপত্তার পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহন করা ছিল একমাত্র এই রাষ্ট্রেরই বিশেষত্ব। শুধু অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ব্যবস্থাই নয়, জনগনের নৈতিক মান উন্নতকরণ,তাহাদের মনে আল্লাহ্র ভয় জাগানো এবং দ্বীন ও শরীয়াত সম্পর্কে তাহাদিগকে সুশিক্ষিত করিয়া তোলার জন্যও নিরন্ততর গুরুত্ব সহকারে চেষ্টা চলানো হইত।
(৭)এই রাষ্ট্রের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হইল আল্লাহ্র নিকট জবাবদিহির তিব্রতম চেতনা।যাহা কিছুই করি না কেন,ব্যক্তিগত কাজ কিংবা জাতীয়-রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন-যে ধরনেই কাজ হউক না কেন-তাহা নিজের ঘরে গোপনে করা হউক,কি প্রকাশ্য-সব কিছুর মূলেই এই চেতনাটি প্রবল হইয়া থাকে। আর এই কারনেই এ রাষ্ট্রের কোন ক্ষেত্রেই আল্লাহ্র নাফরমানী,গণঅধিকার হরণ এবং জুলুম-নির্যাতনের কোন একটি ঘটনাও সংঘটিত হইতে পারিত না। এই দিকটির উপর আতদূর গুরুত্ব আরোপ করা হইত যে, রাষ্ট্রপ্রধান হইতে শুরু করিয়া নিম্নতম সহকারী কর্মচারী নিয়োগে সর্বাধিক আল্লাহভীরু ব্যক্তিকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হইত। ******(আরবী) ‘তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক আল্লাহ্ভীরু ব্যক্তিই তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্র নিকট সর্বাধিক সম্মানার্হ’ এই মূলনীতিই ছিল এই কাজের ভিত্তি।কেননা রাষ্ট্রনেতা বা সরকারী দায়িত্বশীল লোকেরা আল্লাহ্ভীরু না হইলে গোটা জাতিই চরম নাফরমান হইয়া যাইবে। তাহারা নীতিবান না হইলে গোটা জাতিই দুর্নীতিপরায়ণ হইয়া যাইবে-ইহা স্বাভাবিক। রাষ্ট্রনেতা ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ এবং সরকারী কর্মচারীগণ দুর্নীতিপরায়ণ না হইলে সাধারণ মানুষের পক্ষে দুর্নীতিগ্রস্ত হওয়া কক্ষনই সম্ভব হইতে পারে না। এমনকি তাহার ধারণাও করা যায় না। এই কথাটি যেমন সত্য, তেমনি ইহার বিপরীত কথাটিও সত্য। বিশ্বনবী প্রতিষ্ঠিত আদর্শ রাষ্ট্রের এই বৈশিষ্ট্যসমূহ ঐতিহাসিক। ইতিহাসে এইরূপ বৈশিষ্ঠ্যের অধিকারী অন্য কোন রাষ্ট্রেরি নাম খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।
বিশ্বনবী প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র-ব্যবস্থার এই বৈশিষ্ঠ্যসমূহ সম্মুখে রাখিয়া তুলনামূলক আলোচনা করিলে প্রমাণিত হইবে যে, দুনিয়ার অন্যান্য রাস্ত্রের-তাহা রাজনৈতিক হউক কি তথাকথিত ধর্মহীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র,পুজিবাদি রাষ্ট্র হউক কিংবা সমাজাতান্ত্রিক তথা কমিউনিস্ট রাষ্ট্র-কোন একটির সাথেও ইহার কোন তুলনা হয়না। একালের কোন ধরনের রাষ্ট্রই সার্বিক মানবিক কল্যাণের দিক দিয়া বিশ্ব নবী প্রতিষ্ঠিত এই রাষ্ট্রের সমতুল্য হইতে পারে না। দুনিয়ার এসব রাষ্ট্র ব্যবস্থা যেসব নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং মানব-কল্যাণের যেসব বড় বড় দাবি করা হয়, উহার অবৈজ্ঞানিকতা,যুক্তিহীনতা, অমানবিকতা ও অন্তঃসারশূন্যতা বহু পূর্বেই প্রমানিত হইয়াছে। সেসবের ব্যর্থতা সর্বজনস্বীকৃত। কিন্তু বিশ্বনবী প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্রের মূলনীতি যেমন স্বভাবসিদ্ধ,তেমনি শাশ্বত,চিরন্তন।ব্যক্তি মানুষ ও মানবসমষ্ঠির প্রকৃত কল্যাণ কেবল এই ধরনের রাষ্ট্র-ব্যবস্থার মাধ্যমেই অর্জন করা সম্ভব। অন্য কোন ধরনের রাষ্ট্র দ্বারাই ইহা সম্ভব হইতে পারে না।
জীবনের শেষদিন পর্যন্ত বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ(স) এই আদর্শ রাষ্ট্রের পরিচালনা করিয়া গিয়াছেন।‘খিলাফতে রাশেদা’ এই রাষ্ট্রেরই পরবর্তী নাম, ইহারই যথার্থ উত্তরাধিকারী।
খিলাফতে রাশেদা
বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর ইন্তেকালের পর যে চারজন প্রধান সাহাবী ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পালন করিয়াছেন, ইতিহাসে তাহাদিগকেই “খুলাফায়ে রাশেদুন”নামে অভিহিত করা হয় এবং তাঁহাদের পরিচালিত রাষ্ট্র-ব্যবস্থাকেই বলা হয় “খিলাফতে রাশেদা”। ‘খুলাফায়ে রাশেদুনে’র শাসন দীর্ঘকাল স্থায়ী না থাকিলেও বিশ্বের ইতিহাসে তাহা সর্বাধিক মর্যাদা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। শুধু মুসলিম ঐতিহাসিকগণই নহেন,অমুসলিম-এমন কিন মুসলিম-দুশমন ঐতিহাসিকগণও –খুলাফায়ে রাশেদুনের শাসন আমল্কে মানব-ইতিহাসের ‘স্বর্ণ-যুগ’ বলিয়া শ্রদ্ধা জানাইতে বাধ্য হইয়াছেন। বর্তমান পর্যায়ে আমরা ‘খিলাফতে রাশেদার’ বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য ও বৈশিষ্ঠ্য সম্পর্কে আলোচনা করিব।
খিলাফত
‘খিলাফত’ শব্দের আভিধানিক অর্থ ‘প্রতিনিধিত্ব’।ইহার ব্যবহারিক অর্থ, ‘অন্য কাহারো অপসৃত হওয়ার পর তাহার স্থানে উপবেশন করা’। এই শব্দটি স্বতঃই এই কথা প্রমাণ করা যে,উহাই আসল নয়, আসলের প্রতীক মাত্র;কায়া নয় ছায়া,দর্পণের প্রতিবিম্ব।অন্য কথায় মূল পদের স্থলাভিষিক্ত হওয়ারই নাম খিলাফত। ‘ইমাম’ শব্দও এই অর্থেই ব্যবহৃত হয় এবং ‘খলীফা’ ও ‘ইমাম’ এই শব্দদ্বয় একই ব্যক্তির দুইটি স্বতন্ত্র দিককে প্রকাশ করে। পূর্ববর্তী দায়িত্বশীলের প্রতিনিধি ও স্থলাভিষিক্ত হওয়ার দিক দিয়া সে খলীফা এবং সমসাময়িক যুগের জনগণের অনুসরণীয় ও সর্বাধিক গণ্যমান্য হওয়ার কারনে সে ‘ইমাম’ ও ‘নেতা’।বস্তুতঃ পয়গম্বরের স্থলাভিষিক্ত হওয়া এবং তাঁহার অন্তর্ধানের পর গোটা উম্মতের নেতৃত্ব দানকেই বলা হয় ‘খিলাফত’ ও ‘ইমামত’। নবী করীম(স) ইরশাদ করিয়াছেনঃ “তোমাদের পূর্বে বনী ইসরাইল গোত্রের নবী ও পয়গম্বরগণই নেতৃত্ব দান ও রাষ্ট্র পরিচালনা করিতেন;এক পয়গম্বরের অন্তর্ধানের পর আর এক পয়গম্বর আসিয়া তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইতেন। কিন্তু এখন(আমার পর) নবুয়্যাতির ক্রমিকধারা সম্পূর্ণ হইয়াছে(এখন আর কেহ নবী বা রাসূল হইবে না)।অতঃপর তোমাদের মধ্য হইতে খলিফাগণই অগ্রগামী হইবে”।
এই হাদিস হইতে এ কথা পরিস্ফুটিত হইয়া উঠে যে, পয়গম্বরীর প্রতিনিধিত্ব করাকেই খিলাফত বলা হয় এবং ইসলামে নবুয়্যাতের পর ইহাই সর্বাধিক মর্যাদাসম্পন্ন,শ্রদ্ধাভাজন ও পবিত্র দায়িত্বপূর্ণ পদ। এইজন্য ইসলামের ‘খলিফা’গন কুরআন ও সুন্নাতের মূলকে ভিত্তি করিয়া রাষ্ট্র পরিচালনা ও মানব-সমস্যার সমাধানের জন্য যেসব বিধান ও নির্দেশ দান করেন, তাহা অবশ্যই সর্বজনমান্য হইবে। রাসূলে করীম (স) পূর্বাহ্ণেই একথা ঘোষণা করিয়াছেনঃ ‘আমার পর আমার ‘হেদায়েতপ্রাপ্ত’ খলিফাগণকে মানিয়া চলিবে’। এই কারণেই খলীফা নির্বাচন করার সময় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির রাজনৈতিক বিচক্ষণতা ও শাসনতান্ত্রিক জজ্ঞতা-দক্ষতার দিকে যত-না দৃষ্টি দেওয়া উচিত,তদপেক্ষা অধিক লক্ষ্য আরোপ করিতে হইবে নবীর সংস্পর্শে(কিংবা নবীর অবর্তমানে তাঁহার আদর্শ অনুসরণে) তিনি নিজেকে কতখানি পরিশুদ্ধ করিতে সক্ষম হইয়াছেন এবং তাঁহার আধ্যাত্মিক জ্ঞান-বিদ্যা ও নৈতিক বৈশিষ্ট্য কতটুকু আছে,সেই দিকে। হযরত আবূ বকর সিদ্দিক,হযরত উমর ফারুক,হযরত উসমান গনী ও হযরত আলী মুরতাজা(রা)-এই চারজনকে পর্যায়ক্রমে খলীফার পদে নির্বাচন করায় উপরোক্ত নীতির নিগূঢ় তাৎপর্য ও যথার্থতা সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে।
বস্তুতঃইসলামে খিলাফতের দায়িত্ব কর্তব্য অত্যন্ত ব্যাপক ও সর্বাত্মক। যাবতীয় বৈষয়িক,ধর্মীয় ও তামাদ্দুনিক লক্ষ্য উহারই মাধ্যমে অর্জিত হইয়া থাকে।পয়গম্বরের আরব্ধ কার্যাবলীকে সচল ও প্রতিষ্ঠিত রাখা এবং সকল প্রকার সংমিশ্রণ হইতে উহার সংরক্ষণ ও উৎকর্ষ সাধন করা-এই সংক্ষিপ্ত বাক্য দ্বারাই খিলাফতের দায়িত্ব মোটামুটিভাবে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে।আর একটিমাত্র যুক্ত শব্দ দ্বারা ইহা বুঝাইতে হইলে বলা যায়-‘ইক্কামতে দ্বীন’।এই শব্দটিও এত ব্যাপক অর্থবোধক যে,দ্বীন ও দুনিয়ার সব রকমের কাজই উহার মধ্যে শামিল হইয়া যায়। নামায-রোযা,হজ্জ-যাকাত,আইন-কানুন,শাসন-শৃঙ্খলা ও বিচারব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা ও প্রচলন-এক কথায় সমস্ত তামাদ্দুনিক ও আধ্যাত্মিক কাজ সম্পাদনই খিলাফতের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। নবী করীম(স)-এর পবিত্র জীবন এই সব মহান দায়িত্ব সম্পাদনেই অতিবাহিত হইয়াছে। তাঁহার পর যাঁহারা তাঁহার প্রতিনিধি ও স্থলাভিষিক্ত হইয়াছেন,তাঁহারা নিজেদের সমগ্র জীবন এই উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করার জন্নই সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত করিয়াছেন।নবী করিম(স)-এর জীবনকাল হইতেই এইসব কাজে বিভিন্ন লোক জিম্মাদার হিসাবে নিযুক্ত ছিল। নামাযের ইমামতি করার জন্য,সাদকা ও যাকাত আদায় করার জন্য আলাদাভাবে লোক নিয়োগ করা হইয়াছিল। অন্যায় কাজের প্রতিরোধ ও ন্যায় কাজের প্রচার প্রসার এবং জনগণের পারস্পরিক বিবাদ-বিসম্বাদের নিরপেক্ষ বিচার ও ফয়সালার কাজ যোগ্যতাসম্পন্ন লোক দ্বারা সমাধা করা হইত।শত্রুর সহিত মোকাবিলা ও হইত। শত্রুর সহিত মোকাবিলা ও সৈন্য পরিচালনা এবং কুরআন শরীফ শিক্ষাদানের দায়িত্ব স্বতন্ত্র লোকের উপর অর্পিত ছিল। কিন্তু যেহেতু এই যেহেতু এই সমস্ত কাজই খিলাফতের মূল দায়িত্বের মধ্যে শামিল, সেইজন্য স্বতন্ত্রভাবে এইসব দায়িত্ব পালনের উপযোগী যোগ্যতা ও বৈশিষ্ট্য সবই এককভাবে এক খলীফার মধ্যে বর্তমান থাকা একান্তই আবশ্যকীয় ছিল। শুধু তাহাই নয়,আধ্যাত্মিক গুন-বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়া খলীফার মধ্যে নবীসুলভ শিক্ষা ও প্রজ্ঞা বলিষ্ঠভাবে বর্তমান থাকা জরুরী এবং নবী যাহাদের মধ্যে এই ধরনের আধ্যাত্মিক দক্ষতা দেখিতে পান, তাহাদিগকেই নিজের স্থলাভিষিক্ত করার কথা জীবিতাবয়স্থায়ই ইশারা-ইঙ্গিতে প্রকাশ করিয়া যান।অবশ্য অনাকাঙ্ক্ষিত বিশৃঙ্খলা,রক্তপাত ও অবস্থার পরিবর্তন খিলাফতের মূল লক্ষ্যকে চল্লিশ বৎসর পরই ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে এবং উহার কর্তৃত্বভার এমন সব লোকের হস্তে অর্পিত হইয়াছে,যাহারা কোন দিক দিয়াই এই গুরুত্বপূর্ণ পদের যোগ্য ছিল না, একথা অবশ্যই স্বীকার্য। কিন্তু বিশ্বনবীর হেদায়েত অনুযায়ী পরবর্তী খলীফা ও শাসকদের নির্বাচন করা হইলে মানব সমাজের চেহারা সর্বতোভাবে ভিন্ন রকমের হইত,তাহাতে সন্দেহ নাই।
কুরআন ও হাদীস হইতে খলীফার যোগ্যতা-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে যাহা কিছু জানা যায়, উহার দৃষ্টিতে যাচাই করিলে একথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, ‘খুলাফায়ে রাশেদুন’ই ছিলেন মুসলিম জাহানের খলীফা হওয়ার সর্বাধিক উপযোগী। কুরআন হাদীসের বর্ণিত গুন-বৈশিষ্ট্য তাঁহাদের মধ্যে পূর্ণমাত্রায় মওজুদ ছিল এবং সেই কারনে তাঁহারা খিলাফতকে সুষ্ঠু নীতিতে পরিচালিত করিতে পারিবে বলিয়া জনমনে পূর্ণ আস্থা বিদ্যমান ছিল।খিলাফতে রাশেদার দায়িত্ব পালনের জন্য কুরআনের দৃষ্টিতে নিম্নলিখিত গুন-বৈশিষ্ট্য অপরিহার্য মনে করা হইয়াছে। অতএব,নবী করীম(স)-এর পরে যাহাদের মধ্যেই এই গুণাবলী পরিস্ফুট হইবে,তাহারাই সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইবে।
(১)খলীফাকে প্রথম পর্যায়ের ‘মুহাজির’ হইতে হইবে এবং হোদাইবিয়ার সন্ধি,বদর ও তবুক যুদ্ধে শরীক ও সূরায়ে নূর অবতীর্ণ হওয়ার সময় উপস্থিত ছিলেন-এমন হইতে হইবে;
(২)বেহেশতবাসি হইবার সুসংবাদপ্রাপ্তদের মধ্যে গণ্য হইতে হইবে;
(৩)সিদ্দীক,শহীদ প্রভৃতি ইসলামী সমাজের উচ্চ পর্যায়ের লোকদের মধ্যে গণ্য হইতে হইবে।
(৪)নবী করীম(স)-এর কোন ব্যাবহার, কাজ বা কথা দ্বারা একথা প্রমাণিত হইতে হইবে যে,তিনি নিজে কাহাকেও খলীফা নিযুক্ত করিলে তাহাকেই নিযুক্ত করিতেন।
(৫)আল্লাহ্ তা’আলা রাসূলের নিকট যেসব ওয়াদা করিয়াছেন, তাহা তাঁহার সত্তা দ্বারা বাস্তবায়িত হওয়া সম্ভব হইতে হইবে।
(৬)তাঁহার কথা ইসলামী শরীয়াতে প্রমাণিত হইতে হইবে।
এই গুণাবলির বিচ্ছিন্নভাবে অসংখ্য সাহাবীর মধ্যে বর্তমান ছিল; কিন্তু এইগুলির পূর্ণ সমন্বয় ঘটিয়াছিল মাত্র চারজন সাহাবীর মধ্যে।ইঁহারা প্রথম পর্যায়ের মুহাজির ছিলেন,হোদাইবিয়া চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার সময় ইঁহারা উপস্থিত ছিলেন;বদর,ওহোদ,তবুক ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ জিহাদ-সংগ্রামে ইঁহারা ছিলেন অগ্রবর্তী।এইভাবে খিলাফতের যোগ্যতার জন্য অপরিহার্য গুণাবলির মধ্যে কোন একটি হইতেও ইঁহারা বঞ্চিত ছিলেন না। উপরন্তু ইঁহাদের প্রত্যেকেই সম্পর্কেই রাসূলে করীম(স)-এর সুস্পষ্ট মর্যাদাপূর্ণ ভবিষ্যদ্বাণী নির্ভরযোগ্য সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে।হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) সম্পর্কে নবী করীম (স)বলিয়াছেনঃ ‘আমার উম্মাতের মধ্যে তুমিই সর্বপ্রথম বেহেশতে প্রবেশ করিবে। ‘হাওযে-কাওসারে’ তুমিই হইবে আমার সঙ্গী;কেননা পর্বত গহ্বরে তুমিই আমার সাথী ছিলে’। হযরত উমর(রা) সম্পর্কে নবী করীম(স)-এর এই উক্তি বর্ণিত হইয়াছেঃ ‘উমরের কামনায়ই অসংখ্য আয়াত নাজিল হইয়াছে’।হযরত উস্মান(রা) সম্পর্কে রাসূল (স) বলিয়াছেনঃ ‘ফিরেশতাও যাহাকে সম্মান-শ্রদ্ধা জানায়,আমি কি তাঁহাকে সম্মান না জানাইয়া পারি?’ আরও বলিয়াছেনঃ ‘প্রত্যেক নবীরই বন্ধু থাকে,বেহেশতে উসমান হইবে আমার বন্ধু’।হযরত আলী(রা) সম্পর্কে নবী করীম(স)ইরশাদ করিয়াছেনঃ ‘তোমার সঙ্গে আমার হারুন ও মূসার ন্যায় সম্পর্ক স্থাপিত হউক, ইহা কি তুমি চাও না?আল্লাহ্ ও রাসূল যাহার প্রিয়পাত্র, আমি আগামীকাল তাঁহার হস্তেই ঝাণ্ডা তুলিয়া দিব’। এতব্দ্যতীত নবী করীম (স) ইহাদের গুণ-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আরো অনেক মূল্যবান কথাই বলিয়াছেন।সেইসব কথা দ্বারা একথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে,হযরতের দৃষ্টিতে তাঁহার অন্তর্ধানের পর ইঁহারাই ছিলেন খিলাফতের পদে নির্বাচিত হইবার সর্বাধিক উপযুক্ত এবং অধিকারী।
খিলাফতের মৌল আদর্শ
খিলাফত সম্পর্কিত আলোচনাকে গভীর ও ব্যাপকভাবে অনুধাবন করার জন্য উহার রাষ্ট্র-রূপকে যাচাই করা অত্যন্ত জরুরী। এই ব্যাপারে সর্বপ্রথম নেক চরিত্রবিশিষ্ট লোকদের প্রতিই এই ওয়াদা ঘোষিত হইয়াছে। তাই রাষ্ট্রের প্রতিটি(মুসলিম) নাগরিকই খলীফা মর্যাদাসম্পন্ন এবং খিলাফতের দায়িত্ব পালনের সমান সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার অধিকারী। এক্ষেত্রে কেবলমাত্র ব্যাক্তিগত চরিত্র,মানবীয় গুন-বৈশিষ্ট্য ও তাকওয়ার-পরহেজগারীর ভিত্তিতেই মানুষের মধ্যে পার্থক্য করা যাইবে।
তৃতীয়তঃ মানবতার ইতিহাসে যখনি আল্লাহ্র সার্বভৌমত্বের ভিত্তিতে কোন খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে সেখানেই সমাজের মধ্য হইতে কেবলমাত্র সর্বাধিক নেক ও পরহেজগার এবং উন্নত-আদর্শ চরিত্রবান লোকেরাই খলীফা হওয়ার-রাষ্ট্র পরিচালনা করার সুযোগ লাভ করিয়াছে। আর সাধারণ জনতা আল্লাহ্র দেওয়া মৌলিক অধিকার পূর্ণ ইনসাফ ও নিরপেক্ষভাবে ভোগ করিতে পারিয়াছে। কাহারও ক্ষেত্রে সেই অধিকারের এক বিন্দু হরণ করা কিংবা সংকুচিত করা হয় নাই,কাহারো স্বাভাবিক কর্মপথে বিন্দুমাত্র প্রতিবন্ধকতারও সৃষ্টি করা হয় নাই;বরং প্রত্যেকের স্বাভাবিক ক্ষমতা ও প্রতিভাকে আল্লাহ্র আইনসম্মত পন্থায় উৎকর্ষ ও ক্রমবিকাশ লাভের সুযোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।
ইসলামের বিধান অনুযায়ী প্রত্যেক বাক্তিই আল্লাহ্র নিকট জওয়াবদিহি করিতে বাধ্য। এই ব্যাপারে কাহাকেও অতি-মানবের আসনে বসাইয়া আল্লাহ্র সহিত শরীক করা যাইতে পারে না। ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান,খলীফা বা ‘আমিরুল মু’মিনীন’ পদে নির্বাচিত হওয়ার ব্যাপারে প্রত্যেক মুসলিম নাগরিকেরই সমান অধিকার রহিয়াছে। এক্ষেত্রে পদপ্রার্থী হওয়ার কিংবা পদলাভের জন্য চেষ্টা করার অধিকার যেমন কাহারো নাই, তেমনি নাগরিকদের অবাধ সম্মতিতে নির্বাচিত হইলে দায়িত্ব পালনেও সকলেই বাধ্য। খলীফা নির্বাচিত হওয়ার পর তাঁহার মর্যাদায় শুধু এতটুকু পার্থক্য ঘটে যে,জনগন নিজ নিজ খিলাফতের মর্যাদা ও অধিকার তাঁহার হস্তে অর্পণ করিয়াছে মাত্র।কেবল সে-ই খলীফা, অন্য কেহ খলীফা নয়, ইসলামী আদর্শবাদের দৃষ্টিতে একথা কিছুমাত্র সত্য নয়। খিলাফতের শক্তি নাগরিকদের সামাজিক ও সামগ্রিক নিয়ম-শৃঙ্খলা সংরক্ষণ ও অপরিহার্য আইন-কানুন জারিকরণের দায়িত্ব পালনে সর্বতোভাবে নিয়োজিত থাকে। এই শক্তির সংহতি বিধান ও ইহাকে সুনিয়ন্ত্রনে রাখার জন্য ইহা সাধারনের নির্বাচিত ও সর্বাধিক যোগ্যতম ব্যক্তির সত্তায় কেন্দ্রিভূত হওয়া আবশ্যক।
খলীফা বা ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচনের সময় ব্যক্তির জ্ঞান-বুদ্ধি, শিক্ষা-দীক্ষা,মন-মানস,বিচক্ষণতা ও সাংগঠনিক-যোগ্যতাই শুধু দেখিলে চলিবে না, তাহার চরিত্র কত পবিত্র,নির্ভরযোগ্য ও আস্থাভাজন,বিশেষ গুরুত্ব সহকারে তাহাও লক্ষ্য করিতে হইবে।
ইসলামী জীবন-ব্যবস্থা খলীফাকে ‘মাসুম’ বা নিস্পাপ ঘোষণা করে নাই।খলীফাকে নিস্পাপ ও নির্ভুল মনে করিয়া লওয়ারও কোন যুক্তি নাই। প্রতিটি মুসলিমই তাহার কেবল সরকারী দায়িত্ব পালন ও কার্য সম্পাদন সম্পর্কেই নহে,তাহার পারিবারিক ও ব্যক্তিগত জীবন-ধারারও সমালোচনা করিতে পারে।আইনের দৃষ্টিতে তাহার মর্যাদাও হইবে সাধারণ নাগরিকের সমান।আদালতে তাহার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা দায়ের করা যাইতে পারে এবং সে সাধারণ নাগরিকদের মতই বিচারকের সম্মুখে হাযির হইতে বাধ্য। সেখানে তাহাকে তথায় কোন প্রকার বিশিষ্টতা দান করা হইবে না।
খলীফার প্রতি আল্লাহ্র কোন অহি নাজিল হয় না; সুতরাং কুরআন ও সুন্নাহর ব্যাখ্যা-বাস্তবায়নের ব্যাপারে সে কোন বিশেষ মর্যাদা পাওয়ার দাবি করিতে পারে না।
খলীফা কেবল নিজস্ব মত অনুসারেই কার্য সম্পাদন করিতে পারে না,জনসমর্থিত ও যোগ্য-সুদক্ষ ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত মজলিসে শূরা’র(Parliament) সহিত পরামর্শ করিয়াই তাহাকে যাবতীয় কাজ সম্পাদন করিতে হইবে। মজলিসে শূরার সংখ্যাগরিষ্ঠ মত অনুসারেই সিদ্ধান্ত গ্রহন করিতে হয়,এ কথা ঠিক;কিন্তু তাহা সত্ত্বেও সংখ্যাধিক্য খিলাফতী শাসন-ব্যবস্থায় ভাল-মন্দবা করনীয়-বর্জনীয় নির্ধারণের কোন স্থায়ী মানদণ্ড নহে। তাই খলীফা কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে সংখ্যাগুরুর ফয়সালার সহিতও দ্বিমত পোষণ করিতে পারে এবং সে কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে যাহা সত্য বলিয়া প্রত্যয় করিবে,তদনুযায়ী কাজও করিতে পারে।অবশ্য এই সমগ্র ক্ষেত্রেই মুসলিম জনতা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করিবেঃখলীফা সামগ্রিকভাবে কুরআন-সুন্নাহ অনুসারে কাজ করে, না নিজস্ব খেয়ালখুশী অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা প্রয়োগ করে।দ্বিতীয় অবস্থার খলীফা ইসলামী জনতার নিকট হইতে একবিন্দু আনুগত্য পাইবার অধিকার রাখে না,বরং তাহার পদচ্যুতির ব্যবস্থা করাই তাহাদের কর্তব্য হইয়া পড়ে। এইদিক দিয়াও পাশ্চাত্য রাষ্ট্রদর্শন ও শাসনতন্ত্রের সহিত ইসলামী রাষ্ট্রদর্শন ও খিলাফতী গণ-অধিকারবাদের মধ্যে আসমান-জমিন পার্থক্য সুস্পষ্ট।
খুলাফায়ে রাশেদুন
ইতিহাসের যে পর্যায়টি হযরত আবূ বকর সিদ্দীকের(রা) খিলাফত হইতে শুরু করিয়া হযরত আলী(রা) পর্যন্ত বিস্তৃত, ইতিহাসে তাহাই হইতাছে ‘খিলাফতে রাশেদা’র যুগ। আর ৬৩২ ঈসায়ী(১১ হিজরী) হইতে ৬৬১ ঈসায়ী (৪০ হিজরী) পর্যন্ত মুসলিম জাহানের যাঁহার রাষ্ট্রনেতা ছিনেল,তাহাদিগকেই ‘খুলাফায়ে রাশেদুন’ বলিয়া অভিহিত করা হয়।ইঁহাদের মোট সংখ্যা চার এবং ইঁহাদের খিলাফত কালের মোট মুদ্দৎ ত্রিশ বৎসর মাত্র।(অবশ্য উমার ইবনে আব্দুল আজীজ (র)ও ইসলামী খিলাফতের নিয়ম অনুযায়ী নির্বাচিত ও দায়িত্ব পালনে সক্ষম হওয়ায় তিনিও ‘খুলাফায়ে রাশেদ’ রূপে গণ্য)
নবী করীম (স) যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন পর্যন্ত নবুয়্যাত,আইন প্রণয়ন,সর্ব ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দান,বিচার বিভাগ ও সৈন্য বাহিনী পরিচালনা এবং দেওয়ানী সরকারের যাবতীয় দায়িত্বপূর্ণ পদ হযরতের একক ব্যক্তিসত্তায় কেন্দ্রীভূত ছিল; তিনি একাই এই সমস্ত কাজের কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব করিতেন।তাঁহার ইন্তিকালের পর তাঁহার স্থলাভিষিক্ত কে হইবে, এই প্রশ্ন ইসলামী জনতার সম্মুখে অত্যন্ত প্রকট হইয়া দেখা দেয়।যেহেতু নবুয়্যাতের সমাপ্তি হইয়া গিয়াছে-অতঃপর কেহই নবী হইবেন না; কিন্তু রাসূলের স্থলাভিষিক্ত যে হইবে তাহাকে এই নবুয়্যাত ছাড়া ও নবুয়্যাত ব্যতিত আর সমস্ত দায়িত্বই পূর্বানুরুপ আঞ্জাম দিতে হইবে-এই কারনেও এই প্রশ্ন অত্যন্ত বেশি গুরুত্ব সহকারে নেতৃস্থানীয় ভাবিত ও বিব্রত করিয়া তোলে।নবী করীম(স)-এর নবুয়্যাত ও স্বভাব সুলভ নেতৃপদের উত্তরাধিকারী কেহই হইতে পারে না।অন্যদিকে তাঁহার কোন পুত্র-সন্তানও জীবিত ছিলনা।থাকিলেও তাহাতে খলীফা নির্বাচন সমস্যার কোন সমাধানই হইতে পারিত না। কাজেই এই দুইটি প্রশ্ন জটিলভাবে মাথা চাড়া দিয়া উঠিয়াছিলঃ
১-খলীফা কোন পরিবার বা গোত্র হইতে হইবে?
২-খলীফা নিয়োগের পন্থা কি হইবে?
কুরআন মজীদের কোথাও খিলাফতকে কোন বংশ বা গোত্রের জন্য বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয় নাই। হাদীসে যেখানে *****(আরবী)- ‘নেতা বা খলীফা কোরাইশদের মধ্য হইতে নিযুক্ত করিতে হইবে’ বলিয়া উল্লেখ পাওয়া যায়,সেখানেও স্পষ্ট ভাষায় নির্দেশ রহিয়াছেঃ
‘তোমাদের উপর কোন হাবশী গোলামও শাসক নিযুক্ত হইলে তোমারা তাহার অবশ্যই আনুগত্য করিবে’। কাজেই এতদুভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের পন্থা অনুসন্ধান করা আবশ্যক। একটু গভীর ও সুক্ষ দৃষ্টিতে চিন্তা করলেই বুঝিতে পারা যায় যে,মূলতঃএই দুইটি হাদিসই সত্য ও বাস্তব তত্ত্ব-ভিত্তিক ঘোষণা।ইসলামে খিলাফতকে কোন বংশ-গোত্র পরিবার কিংবা কোন ব্যক্তি বা শ্রেণীর জন্য বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয় নাই, এ-কথা চিরন্তন সত্য। ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় সকল সময় ও অবস্থায়ই এই মূলনীতি অনুযায়ী কাজ হইতে হইবে,ইহাতে সন্দেহ নাই;কিন্তু নবী করীম (স)যে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তাহাঁরই অব্যবহিত পড়ে উহার দায়িত্বভার পালনের জন্য কুরাইশ বংশের লোক অপেক্ষা অপর কোন বংশের লোক যে কিছুমাত্র যোগ্য বা দক্ষতাসম্পন্ন ছিল না, তাহাও এক অনস্বীকার্য ঐতিহাসিক সত্য।খিলাফতে রাশেদার ও ইহার পরবর্তী কালের ইতিহাসই এই কথার সত্যতা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে।কাজেই খিলাফতে রাশেদার চারজন খলীফাই কুরাইশ বংশের লোকদের মধ্য হইতে নির্বাচিত হওয়া সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত হইয়াছে। কেননা তাহা না হইলে তদানীন্তন আরব-সমাজের মধ্য হইতে বিশেষ যোগ্যতা ও দক্ষতা সহকারে খিলাফতের দায়িত্ব পালন করা অপর কাহারো পক্ষেই সম্ভব হইত না। কিন্তু ইহা কোন চিরন্তন ও শাশ্বত নিয়ম নহে; ‘খিলাফতে রাশেদা’র পরও খলীফার কুরাইশ বংশোদ্ভূত হওয়ার কোন শর্তই ইসলামী রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় স্বীকৃত নয়।১ {বলা বাহুল্য, ইসলামী রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরাও এই ধরনের কোন শর্তের কথা উল্লেখ করেন নাই।}
খলীফা নির্বাচনের বাস্তব ও সুস্পষ্ট কোন পদ্ধতি কুরআন-হাদীসে উল্লেখিত হয় নাই।মনে হয়,সেজন্য কোন বিশেষ পন্থাকে স্থায়ীভাবে স্বীকার করিয়া লওয়া এবং যুগ-কাল-স্থান-নির্বিশেষ সর্বত্র উহার অনুসরণকেই গোটা উম্মতের উপর বাধ্যতামূলকভাবে চাপাইয়া দেওয়া ইসলামের শাশ্বত বিধানের লক্ষ্য নয়। এই জন্য নির্বাচনের কোন বিশেষ পদ্ধতির(Form or Process) পরিবর্তে একটি শাশ্বত মূলনীতি পেশ করা হইয়াছে।বলা হইয়াছেঃ*****(আরবী) “ইসলামী আদর্শবাদীগণ নিজেদের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ পারস্পরিক পরামর্শের মাধ্যমে সম্পন্ন করিয়া থাকে’। আর রাষ্ট্রপ্রধান বা খলীফা নির্বাচনই যে মুসলিম সমাজে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় ও সামষ্ঠিক ব্যাপার এবং মুসলিম জনতার অবাধ রায় ও পরামর্শের ভিত্তিতেই যে ইহা সুসম্পন্ন হওয়া উচিত,তাহাতে কাহারো দ্বিমত থাকিতে পারে না। অতএব, জনমতের ভিত্তিতে খলীফা নির্বাচন করিতে হইবে- ইহাই হইল ইসলামী নির্বাচনের একমাত্র মূলনীতি। এই নীতিকে মুসলিম উম্মত বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কিভাবে প্রয়োগ করিয়াছে ও নির্বাচন-সমস্যার সমাধান করিয়া লইয়াছে,এখন তাহাই আমাদের বিচার্য।
খুলাফায়ে রাশেদুনের নির্বাচন
খলীফা নির্বাচনের উপরোল্লেখিত মূলনীতিকে খুলাফায়ে রাশেদুনের নির্বাচনের ব্যাপারে নিম্নলিখিত রূপে প্রয়োগ করা হইয়াছেঃ
(১)নবী করীম (স)-এর ইন্তেকালের পর মুসলিম উম্মতের দায়িত্বশীল নাগরিকগন ‘সকীফায়ে বনী সায়েদা’ নামক(টাউন হল কিংবা পরিষদ ভবনের সমমর্যাদাসম্পন্ন)স্থানে মিলিত হন এবং প্রকাশ্যভাবে দীর্ঘ ও বিস্তারিত আলোচনার পর সর্বসম্মতিক্রমে হযরত আবূ বকর(রা)-কে খলীফা নির্বাচিত করেন।উপস্থিত জনতা তখন-তখনি অকুণ্ঠিতভাবে তাঁহার আনুগত্যর শপথ(বায়’আত) গ্রহন করে এবং খলীফা নির্বাচিত হইয়াই তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব,কর্তব্য ও নীতি-নির্ধারকমূলক ভাষণ দান করেন।
(২)হযরত উমর ফারুক(রা)-এর নির্বাচনে স্বতন্ত্র পদ্ধতি অবলম্বিত হইয়াছে।প্রথম খলীফা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক(রা) তাঁহার গোটা ইসলামী জিন্দেগী ও খলীফা-জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী তথা বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে বুঝিতে পারিয়াছেন যে, তাঁহার পর খলীফা হওয়ার উপযুক্ত ব্যক্তি সমগ্র জাতির মধ্যে হযরত উমর(রা)অপেক্ষা দ্বিতীয় কেহ বর্তমান নাই।তাঁহার খিলাফতকালীন যাবতীয় ঘটনা ও গুরুত্বপূর্ণ সরকারী ও বেসরকারী কাজে হযরত উমর(রা)নিবিড়ভাবে শরীক ছিলেন;কুরআন মজীদ সঞ্চয়ন ও গ্রন্থাবদ্ধকরণও কেবলমাত্র তাহাঁরই ঐকান্তিক আগ্রহ,চেষ্টা ও পরামর্শে সম্পন্ন হইয়াছিল।হযরত আবূ বকর(রা)নিজের অভিজ্ঞতা ও প্রধান সাহাবাদের সহিত পরামর্শক্রমে হযরত উমর ফারুক(রা)-কেই পরবর্তী খলীফা নির্বাচনের জন্য মুসলিম জনতার নিকট সুপারিশ করিয়া গেলেন।মুসলিম জনসাধারন প্রথম খলীফার সুপারিশ ও নিজেদের নিরপেক্ষ ও অকুণ্ঠ রায়ের ভিত্তিতে হযরত উমর(রা) –কেই খলীফা হিসাবে নির্বাচিত করিল ও তাঁহার হস্তে বায়আত গ্রহন করিল।উমর (রা) খলীফা নির্বাচিত হইয়াই তাঁহার পূর্বসূরীর ন্যায় মুসলিম জনতাকে সম্বোধন করিয়া নীতি-নির্ধারণী ভাষণ দান করেন।
(৩)দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর(রা) যখন বুঝিতে পারিলেন যে,তাঁহার জীবন-পাত্র সম্পূর্ণ হইতে চলিয়াছে,তিনি আর বেশিক্ষন বাঁচিয়া থাকিতে পারিবেন না, তখন তিনি নিজের স্থলাভিষিক্ত ও পরবর্তী খলীফা নির্বাচনের প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন। সে জন্য তিনি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পদ্ধতি অবলম্বন করেন।তিনি ছয়জন শ্রেষ্ঠ ও নেতৃস্থানীয় সাহাবীর সমন্বয়ে একটি ‘নির্বাচনী বোর্ড’- আধুনিক পরিভাষায় ‘নির্বাচন কমিশন’-নিযুক্ত করিলেন।অন্যান্যদের ছাড়াও হযরত উসমান ও হযরত আলী(রা)ও এই বোর্ডের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।তাঁহার দৃষ্টিতে এই ছয় জনই খিলাফতের জন্য যোগ্য ব্যাক্তি ছিলেন। তিনি আদেশ করিলেন যে,তাঁহার অন্তর্ধানের পর তিন দিনের মধ্যেই যেন এই বোর্ড নিজেদের মধ্য হইতে সর্বাধিক যোগ্য ব্যক্তিকে খলীফা নির্বাচন করে।বোর্ড সুষ্টুরূপে তাহার দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করে এবং এই ব্যাপারে নিকটবর্তী ও দূরবর্তী মুসলিম নাগরিকদের রায় সংগ্রহ করে।মদীনার প্রতিটি ঘরে উপস্থিত হইয়া পুরুষদের সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রী লোকদেরও রায় জিজ্ঞাসা করা হয়।দূরাগত ব্যবসায়ী ও পর্যটকদের নিকটও রায় জিজ্ঞাসা করিতে ত্রুটি করা হয় নাই।এইভাবে ইসলামী নাগরিকদের সর্বাধিক রায় ও আলাপ-আলোচনার পর হযরত উসমান(রা)-কেই তৃতীয় খলীফা পদে নির্বাচিত করা হয়।
(৪)তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান(রা)-এর শাহাদাতের পর মদীনার পরিবেশ ফিতনা-ফাসাদের ঘনঘটায় অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। মিশর,কুফা ও বসরার বিদ্রোহীগণ মদীনায় প্রবল তাণ্ডবের সৃষ্টি করে।তখন প্রধান সাহাবীদের অধিকাংশই সামরিক ও সাংগঠনিক দায়িত্ব পালনের জন্য রাজধানীর বাহিরে অবস্থান করিতেছিলেন।এই অবস্থায় হযরত উসমান (রা)-এর শাহাদাতের পর ক্রমাগত তিন দিন পর্যন্ত খলীফার পদ শূন্য থাকে।শেষ পর্যন্ত দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পর হযরত আলী(রা)-কেই খলীফা নির্বাচিত করা হয়।
এই বিশ্লেষণ হইতে একথা প্রমাণিত হয় যে, খুলাফায়ে রাশেদুনের নিয়োগ ও নির্বাচনের ব্যাপারে একই ধরনের বাহ্যিক পদ্ধতি(Form Of Election)অনুসৃত না হইলেও প্রতিটি পদ্ধতিতেই জনমতকে নির্বাচনের ভিত্তিরূপে স্বীকার করা হইয়াছে এবং কোন ক্ষেত্রেই জনমতকে উপেক্ষা করা হয় নাই।বস্তুতঃপ্রকৃত খিলাফতের ইহাই মৌলিক ভাবধারা এবং জনগণের অধিকার সংরক্ষণ ও রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য প্রতিটি যুগে ও অবস্থায়ই ইহা কার্যকর হওয়া একান্ত অপরিহার্য। উপরন্তু মৌলিক ভাবধারাকে যথোপযুক্ত মর্যাদা ও গুরুত্ব সহকারে রক্ষা করিয়া রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচনের যে কোন বাহ্যিক পদ্ধতি গ্রহন করা যাইতে পারে।কেননা ইসলামে বাহ্যিক অবয়ব ও আকার-আকৃতির বিশেষ গুরুত্ব নাই;বরং জাতীয় ও তামদ্দুনিক ব্যাপারে উহার মৌলিক ভাবধারাই হইতেছে একমাত্র লক্ষ্য রাখার বস্তু।
খিলাফতে রাশেদার বৈশিষ্ট্য
ইতিহাস দর্শনের দৃষ্টিতে খিলাফতে রাশেদার ত্রিশ বৎসরকালীন শাসন ব্যবস্থার পর্যালোচনা করিলে উহার নিন্মলিখিত বৈশিষ্ট্যসমূহ গোটা মানব জাতিকে আকৃষ্ট ও বিমোহিত করেঃ
(১)খুলাফায়ে রাশেদুনের আমলে বিশ্বনবীর পবিত্র আদর্শ উজ্জল অনির্বাণ প্রদীপে পরিণত হইয়াছিল এবং সমগ্র পরিমণ্ডলকে উহ্য নির্মল আলোকচ্ছটায় উদ্ভাসিত করিয়া রাখিয়াছিল। খলীফাদের প্রতিটি কাজ ও চিন্তায় উহার গভীর প্রভাব বিদ্যমান ছিল।চারিজন খলীফাই বিশ্বনবীর প্রিয়পাত্র,বন্ধু ও বিশিষ্ট সহকর্মী ছিলেন।অপরাপর সাহাবীদের তুলনায় রাসূলের সাহচর্য ইঁহারাই সর্বাধিক লাভ করিয়াছিলেন।ইঁহারা ছিলেন হযরতের বিশ্বস্ত ও পরীক্ষিত এবং তাঁহার উদ্দেশ্যে উৎসর্গকৃত প্রাণ।একমাত্র হযরত আলী(রা) ব্যতিত আর তিনজন খলীফাই নবী করীম(স)-এর দ্বিতীয় কর্মকেন্দ্র ও শেষ শয্যাস্থল মদীনায় রাজধানী রাখিয়াই খিলাফতের প্রশাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করিয়াছিলেন।
(২)খিলাফতে রাশেদার অন্তর্ভুক্ত কোন খলীফার বংশ-গোত্র কিংবা পরিবার-ভিত্তিক অধিকার,উত্তরাধিকার বা প্রাধান্যের কোনই অবকাশ ছিল না। চারিজন খলীফা তিনটি স্বতন্ত্র পরিবার হইতে উদ্ভুত ছিলেন।বস্তুতঃইঁহারাই ছিলেন গোটা ইসলামী জনতার সর্বাপেক্ষা অধিক আস্থাভাজন।ক্রমিক পর্যায়ে ইঁহাদের নির্বাচনে প্রকৃত জনপ্রতিনিধিত্বের মৌলিক ভাবধারা কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই;বরং উহাই রক্ষিত হইয়াছে সর্বতোভাবে।তখন আধুনিক কালের পদ্ধতিতে নিরপেক্ষ সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইলেও কেবলমাত্র তাঁহারাই যে সর্বাধিক ভোটে নির্বাচিত হইতেন,তাহাতে কোনই সন্দেহ থাকিতে পারে না।
(৩)খিলাফতে রাশেদার আমলে আইন রচনার ভিত্তি ছিল কুরআন ও সুন্নাহ।যে বিষয়ে তাহাতে কোন সুস্পষ্ট নির্দেশ পাওয়া যাইত না,সে বিষয়ে ইজতিহাদ পদ্ধতিতে রাসূলের আমলের বাস্তব দৃষ্টান্ত ও অনুরূপ ঘটনাবলির সামঞ্জস্যের প্রতি লক্ষ্য রাহিয়া ইহার সমাধান বাহির করা হইত এবং এই ব্যাপারে কুরআন ও হাদীস পারদর্শী প্রতিটি নাগরিকেরই রায় প্রকাশের সমান অধিকার স্বীকৃত ছিল।কোন বিষয়ে সকলের মতৈক্যের সৃষ্টি হইলেই,সে সম্পর্কে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হইত।ফিকাহ-শাস্রের পরিভাষায় ইহাকেই বলা হয় ইজমা। ইসলামী শরিয়াতে ইহা সর্বজনমান্য মূলনীতি বিশেষ।আর কোন বিষয়ে মতবৈষম্যের সৃষ্টি হইলে খলীফা কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে নিজস্ব রায় অকুণ্ঠিতভাবে প্রকাশ করিতেন এবং তদানুযায়ী কার্য সম্পাদন করিতেন।
(৪)খুলাফায়ে রাশেদুন অধিকাংশ ব্যাপারেই দায়িত্বশীল সাহাবীদের সহিত পরামর্শ করিতেন।সাধারণ ব্যাপারে তাঁহারাই মনোনয়ন অনুযায়ী ‘মজলিসে শুরা’র সদস্য নিযুক্ত হইতেন।কিন্তু রায়দানের অধিকার কেবলমাত্র নিযুক্ত সদস্যদের জন্যই নির্দিষ্ট ছিল না।
(৫)খুলাফায়ে রাশেদুনের আমলে রাজকীয় জাঁক-জমক ও শান-শকাতের কোন স্থান ছিল না।সাধারণ নাগরিকদের ন্যায় অতি সাধারণ ছিল খলীফাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা।তাঁহারা প্রকাশ্য রাজপথে একাকী চলাফেরা করিতেন;কোন দেহরক্ষী তো দূরের কথা,নামে মাত্র পাহারাদারও ছিল না।প্রতিটি মানুষই অবাধে খলীফার নিকট উপস্থিত হতে পারিত।তাহাদের ঘরবাড়ি ও সাজ-সরঞ্জাম ছিল সাধারণ পর্যায়ের।
(৬)খুলাফায়ে রাশেদুন ’ বায়তুল মাল বা রাষ্ট্রের অর্থ ভাণ্ডারকে জাতীয় সম্পদ ও আমানতের ধন মনে করিতেন।রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে মঞ্জুরী ব্যতীত নিজের জন্য এক করা-ক্রান্তি পর্যন্তও কেহ খরচ করিতে পারিতেন না।এতব্দ্যতীত নিজেদের পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনের জন্যও তাঁহারা নিজেদের ক্ষমতা ও পদাধিকার বলে বায়তুল মাল হইতে কিছুই ব্যয় করিতেন না।
(৭)তাঁহারা নিজেদেরকে জনগণের খাদেম মনে করিতেন।কোন ক্ষেত্রেই তাঁহারা নিজদগকে সাধারণ লোকদের অপেক্ষা শ্রেষ্ট ধারণা করিতেন না। তাঁহারা কেবল রাষ্ট্রীয় পর্যায়েই জননেতা ছিলেন না, নামায ও হজ্ব প্রভৃতি ধর্মীয় ব্যাপারেও যথারীতি তাঁহারাই নেতৃত্ব দিতেন।
খিলাফতে রাশেদার আমলে ধর্মীয় কাজের নেতৃত্ব ও রাষ্ট্রীয় কাজের কর্তৃত্ব বিচ্ছিন্ন ও বিভক্ত ছিল না;বরং এই উভয় প্রকার নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বই একজন খলীফার ব্যক্তি সত্তায় কেন্দ্রীভূত ও সমন্বিত হইয়াছিল।বস্তুতঃধর্ম ও রাজনীতির পৃথকীকরণ এবং ধর্মীয় কাজ ও রাষ্ট্রীয় কাজে দ্বৈতবাদ যেমন আধুনিক পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য, অনুরুপভাবে এতদুভয়ের একত্রীকরণ ও সর্বতোভাবে একমুখীকরণই ছিল খিলাফতে রাশেদার বৈশিষ্ট্য।
খিলাফতে রাশেদার রাশেদার রাষ্ট্র-রূপ
হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) খলীফা নির্বাচিত হওয়ার পর এক ব্যক্তি তাঁহাকে ******- ‘হে আল্লাহ্র খলীফা’ বলিয়া সম্বোধন করিলে তিনি সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিলেনঃ ‘আমি আল্লাহ্র খলীফা নহি,আমি আল্লাহ্র রাসূলের খলীফা’।
ঐতিহাসিকগণ খলীফার এই উক্তিকে তাঁহার স্বভাবসুলভ অতুলনীয় বিনয় ও স্বীয় তুচ্ছতাবোধের অকাট্য প্রমাণ মনে করিয়া লইয়াছেন। কিন্তু রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে কথাটির বিশ্লেষণ করিলে ইহা হইতে ‘খিলাফতে’র গভীর তাৎপর্য সুস্পষ্ট হইয়া উঠে।বস্তুতঃপ্রাথমিক যুগে মুসলমানদের হৃদয়ে খিলাফতের যে রাষ্ট্ররূপ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল,হযরত আবূ বকরের এই উক্তি তাহারই সম্প্রকাশক।
বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর পূর্বে ও পরে কালের স্রোতে শত শত বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে।এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে শত-সহস্র রাজা-বাদশাহ ও দেশ শাসক আসিয়াছে ও দুনিয়ার রঙ্গমঞ্চ হইতে বিদায় নিয়াছে। তাহাদের সম্পর্কে সমসাময়িক লোকদের ও প্রজা-সাদারণের দাবি ছিল,তাহারা ভূ-পৃষ্টে আল্লাহ্র স্থলাভিষিক্ত। এই কারনে তাহারা যে সম্ভ্রম-মর্যাদা ও পবিত্রতার অধিকারী, পৃথিবীর বুকে তাহা অন্য কাহারোই থাকিতে পারে না।মিশরের ফিরাউনী রাজা-বাদশাহদের আত্মাভিমান ও দাম্ভিকতা ঐতিহাসিক ব্যাপার হইয়া রহিয়াছে।একজন ফিরাউন *****(আরবী) ‘আমি তোমাদের প্রধান ও শ্রেষ্ঠ প্রভু’ বলিয়া যে দাবি করিয়াছিল, কুরআন মজিদেও তাহার উল্লেখ রহিয়াছে।দূর অতীতকাল হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত রাষ্ট্রকর্তাদের অধিকাংশই এইরূপ মানসিকতার পরিচয় দিয়া আসিয়াছে। বর্তমান কালেও ইহার দৃষ্টান্ত কিছুমাত্র বিরল নহে।এই ব্যাপারে যাহা কিছু অপূর্ণতা ছিল,প্রত্যেক যুগের তোষামোদকারী ধর্মযাজক ও পুরোহিতরা তাহার সম্পূর্ণ করিয়া তুলিতে একবিন্দু ত্রুটি করে নাই।রাজা –বাদশাহ ও দেশ শাসককে তাহারা ‘পূজ্য’ ও ‘আরাধ্য’ করিয়া তুলিয়াছে যুগে যুগে, দেশে দেশে। মিসর,বেবিলন,পারস্য,ভারতবর্ষ ও অন্যান্য বহু দেশের অবস্থাই ছিল এইরূপ।এইসব দেশের অধিকাংশ রাজা-বাদশাহ ও সর্বোচ্চ ক্ষমতাশালী ব্যক্তি নিজেকে ধরনী তলে ‘খোদার প্রতিনিধি’ বা ‘খোদার ছায়া’ মনে করিত।তাহাদের অসহায় দরিদ্র প্রজাসাধারণও তাহাদিগকে অনুরূপ মর্যাদা দানে কিছুমাত্র ত্রুটি করিত না।
মধ্যযুগের ইউরোপেও পাদ্রীরা রাজা-বাদশাহদের ইঙ্গিতে ও নির্দেশেই তাহাদিগকে মহান,সম্মানার্হ ও পবিত্র বলিয়া উচ্চতম মর্যাদা দান করিতেও কিছুমাত্র সংকোচ বোধ করিত না। এই মর্যাদা তাহারা আল্লাহ্র নিকট হইতে পাইয়াছে বলিয়াই পাদ্রীরা প্রচারণা চালাইত।ইহার ফলে তাহাদের ক্ষমতা হইত অপ্রতিদ্বন্দ্বী-সকল প্রশ্ন,আপত্তি ও সমালোচনার অনেক ঊর্ধ্বে, জনগণের নাগালের বাহিরে; তাহারা ‘খোদার প্রত্যক্ষ প্রতিনিধি’ রূপে বিবেচিত হইত।তাহাদের মুখনিঃসৃত প্রতিটি কথাই ‘খোদার নিকট হইতে অবতীর্ণ প্রত্যাদেশ’ রূপে গণ্য হইত।তাহাদের আদেশ-নিষেধ সরাসরি আল্লাহ্র প্রত্যক্ষ আদেশ-নিষেধ সমতুল্য এবং অবশ্য-মান্য মনে করা হইত।এই কারনে উহা অমান্য করা,প্রত্যাখ্যান করা বা উহার প্রতি বিন্দুমাত্র অবজ্ঞা প্রদর্শন করাও মহাপাপের শামিল হইয়া যাইত এবং তাহা ছিল কার্যতঃঅসম্ভব। পঞ্চদশ শতাব্দী-এবং কোন কোন জাতিতে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত-এই অবস্থাই বিরাজিত ছিল।এই সময় পর্যন্তকার ইউরোপ যদিও জ্ঞান-বিজ্ঞান, সভ্যতা-সংস্কৃতি ও শিল্প-কুশলতায় অনেক উন্নতি লাভ করিয়াছিল; কিন্তু অন্ধ বিশ্বাসের যে ঠুঁলি তাহাদের চক্ষুর উপর বসাইয়া দেওয়া হইয়াছিল, তাহা তখনো অপসারিত হয় নাই। উত্তরকালে ব্যক্তিক ও মানসিক স্বাধীনতা এবং সাম্যবাদের অগ্রসেনারা এইসব মানব ধ্বংসকারী ও মানবিক মর্যাদা হরণকারী রসম-রেওয়াজের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদের আওয়াজ তুলিয়া আকাশ-পাতাল মথিত করেন এবং উহার বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহ করিতে বাধ্য হন।অবশ্য এই অভিযানে হাজার হাজার মানুষকে মহামূল্য জীবনও উৎসর্গ করিতে হইয়াছিল।
রাজা-বাদশাহদের এই পদ-পবিত্রতা ও মহাসম্মানের ভাবধারা বিশ-জাতিসমূহের মধ্যে শত শত বৎসর পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।আজিকার ইউরোপ এই ভাবধারা হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে খুব বেশি দিন হয় নাই। এই প্রেক্ষিতে প্রথম খলীফা হযরত আবূ বকর সিদ্দীকি (রা)- এর উপরোক্ত ক্ষুদ্র উক্তিতে নিহিত বিনয় ও আত্ম-স্বার্থহীনতা বিচার্য। একটি লোক তাঁহাকে ‘খলিফাতুল্লাহ্’- আল্লাহ্র খলীফা বা আল্লাহ্র প্রতিনিধি বলিয়া সম্বোধন করিলে তিনি তাহা মানিয়া লইতে স্পষ্ট ভাষায় অস্বীকার করেন এবং বলেনঃ ‘আমি আল্লাহ্র খলীফা নহি। আমাকে রাসূলের খলীফা বলিয়া অভিহিত করতে পার’।
‘রাসূলের খলীফা’ কথাটিও কোনরূপ ব্যক্তিগত দাপট-প্রতাপ,শান-শওকাত ও শ্রেষ্ঠত্ব-বড়ত্ব বা নিরংকুশ কর্তৃত্ব প্রকাশকারী নয়।উহার মূল তাৎপর্য হইল আল্লাহ্র বিধানের ভিত্তিতে তাঁহারাই নির্ধারিত সীমা-সরহদের মধ্যে থাকিয়া মুসলমানদের নেতৃত্ব দান ও রাষ্ট্র পরিচালনায় রাসূলে করীম(স)-এর স্থলাভিষিক্ত বা প্রতিনিধি হওয়া মাত্র।কিন্তু যেসব বিষয়-ব্যাপার কেবলমাত্র রাসূলের জন্য নির্দিষ্ট, সেসব ক্ষেত্রে তাঁহার ‘স্থলাভিষিক্ত’ হওয়ার কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না,উহার চিন্তা বা ধারণাও ইহাতে স্থান পায় নাই।প্রথম খলীফা নির্বাচিত হওয়ার পর প্রদত্ত প্রথম নীতি-নির্ধারণী ভাষণের একাংশ হইতেই তাঁহার এই কথার সত্যতা প্রতিভাত হইয়া উঠে।ভাষণের সেই অংশটি এইঃ
‘আমাকে খিলাফতের এই দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছে বটে;কিন্তু আমি নিজেকে এই গুরুদায়িত্ব পালনের কিছুমাত্র যোগ্য মনে করি না। আল্লাহ্র শপথ!আমার ঐকান্তিক বাসনা ছিল,তোমাদের মধ্য হইতে অপর ব্যক্তি এই দায়িত্ব গ্রহন করিবে।এখন তোমাদের কেহ যদি মনে করে যে,রাসূলে করীম(স) যে যে কাজ করিয়াছেন সেইসব কাজও আমি করিব,তাহা হইলে মনে রাখিও, এই ধারণা বা আশার কোন ভিত্তি নাই।রাসূলে করীম(স) আল্লাহ্র বান্দাহ ছিলেন,ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।কিন্তু সেই সঙ্গে আল্লাহ্ তা’আলা তাঁহাকে মহান নবুয়্যাত ও রিসালাতের নিয়ামত দানে ধন্য করিয়াছিলেন এবং সরবপ্রকার গুনাহ্-খাতা হইতে তাঁহাকে মুক্ত ও পবিত্র ঘোষণা করিয়াছিলেন’।
‘আমিও আল্লাহ্রই বান্দাহ। কিন্তু তোমাদের মধ্য হইতে কাহারও তুলনায় আমি উত্তম ব্যক্তি নহি।তোমরা আমার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিবে।যদি দেখিতে পাও,আমি আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রদর্শিত পথে চলিতেছি, তাহা হইলে তোমারও আমার অনুসরণ করিতে থাকিবে।কিন্তু তোমার যদি আমাকে ‘সিরাতুল-মুস্তকীম’ হইতে বিচ্যুত ও বিভ্রান্ত দেখিতে পাও তাহা হইলে আমার ভুল ধরাইয়া দিয়া আমাকে সঠিক, সত্য ও সোজা পথে পরিচালিত করিবে’।
বলা নিষ্প্রয়োজন,হযরত রাসূলে করীম (স)-এর ইন্তেকালের পর হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) মুসলিম জনতার নেতৃত্ব ও ইসলামী রাষ্ট্র-সংস্থা পরিচালনার দায়িত্ব নিজ হইতে গ্রহন করেন নাই।উদার-উন্মুক্ত পরিবেশে প্রকাশ্য নির্বাচন এবং গণ-সন্তোষ ও সমর্থন অর্জিত হওয়ার পরই তিনি এই কাজে ব্রতী হইয়াছিলেন। আল্লাহ্ তা’আলা যেভাবে নিজের পক্ষ হইতে নিজের বাছাই ও মনোনয়নের মাধ্যমে হযরত মুহাম্মাদ (স)-কে নবী ও রাসূল বানাইয়াছিলেন,তেমনিভাবে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক(রা) কিংবা পরবর্তী খলিফাত্রয় আল্লাহ্ কর্তৃক মনোনীত হন নাই। তাহারা আল্লাহ্ প্রেরিতও ছিলেন না। অন্যান্য মানুষের তুলনায় তাঁহাদের আদর্শিক শ্রেষ্ঠত্ব ও বিশিষ্টতা সর্বজনজ্ঞাত ও অবশ্য স্বীকৃতব্য; কিন্তু এই শ্রেষ্ঠত্ব ও বিশিষ্টতা আল্লাহ্ কর্তৃক ঘোষিত নয়।দ্বিতীয়তঃইহা তাঁহাদের তাকওয়া পরহেজগারী সদগুণাবলীর অনিবার্য পরিণতি মাত্র।খিলাফতের কারণেও এই বিশিষ্টতা অর্জিত হয় নাই,রাসূল যেমন বিশিষ্ট হইয়াছিলেন নবুয়্যাত ও রিসালাতের কারণে।বস্তুতঃখলীফা পদ নিছক বৈষয়িক, খোদায়ী (Divine) নয়।উহার সহিত অলৌকিক ও খোদায়ীর আদেশ ও নির্দেশ দানের অধিকারী ছিলেন,যাহা আল্লাহ্র নাজিল করা বিধান-ভিত্তিক এবং রাসূলের উপস্থাপিত শিক্ষা ও ব্যাখ্যার সহিত সঙ্গতিপূর্ণ।আল্লাহ্র বিধান-পরিপন্থী ও রাসূলের শিক্ষা ও ব্যাখ্যার সহিত অসঙ্গতিপূর্ণ কোন নির্দেশ দেওয়ার কোন অধিকার যেমন তাঁহাদের ছিল না,তেমনি মুসলমান জনগণও সেই ধরনের কোন নির্দেশ মানিয়া লইতে আদৌও বাধ্য নয়। প্রথম খলীফা নিজেই তাঁহার প্রথম ভাষণে এই কথাটি সুস্পষ্ট করিয়া দিয়া বলিয়াছেনঃ********(আরবী)
আমার আনুগত্য করিতে থাকিবে যতক্ষণ আমি আল্লাহ্ এবং তাঁহার রাসূলের আনুগত্য করিয়া চলিতে থাকিব।কিন্তু আমি নিজেই যদি(আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের)নাফরমানী করি,তাহা হইলে আমার আনুগত্য করা তোমাদের কর্তব্য নয়।
পরবর্তী খলীফাদের উপাধি
হযরত আবূ বকর (রা)-এর পর হযরত উমর ফারুক(রা) খলীফা নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু তিনি নিজে ‘খলীফায়ে রাসূল’-‘রাসূলের খলীফা’নামে অভিহিত হইতে সম্মত হইলেন না। এই বিষয়ে সমাজের লোকদের সহিত পরামর্শ করা হয়।শেষ পর্যন্ত তিনি ‘আমীরুল মু’মিনীন’- ‘মুসলিম জনগণের রাষ্ট্রনেতা ও পরিচালক’ সম্বোধনে সম্মত হইলেন।পরবর্তী খলীফাদ্বয়ও এই সম্বোধনেই ভূষিত হইয়াছেন। ‘খলীফা’ শব্দে অভিহিত হইতে তাঁহারা রাযী হন নাই এইজন্য যে,উহা মানিয়া লইলে ‘খলীফায়ে রাসূল’-‘রাসূলের খলীফা’ এইরূপ সম্বোধনে অভিহিত হইতে হইত। আর ইহার ফলে পরবর্তী খলীফার সম্বোধনে এই শব্দটির পুনরাবৃত্তি ঘটিত তিনবার কিংবা ততোধিকবার আর ইহা অত্যন্ত বিদঘুটে,অশ্রুতি মধুর,অমার্জিত এবং নিতান্তই অশোভন হইয়া পড়িত।
হযরত উমর(রা)-এর ‘খলীফায়ে রাসূল’উপাধিতে ভূষিত হওয়ার পরিবর্তে ‘আমিরুল মু’মিনীন’ নামে সম্বোধিত হইতে সম্মৎ হওয়ার মূলে আরো একটি কারন নিহিত ছিল।হযরত আবূ বকর সিদ্দিকী (রা) যখন বলিয়াছিলেন,আমি আল্লাহ্র খলীফা নহি,আল্লাহ্র রাসূলের খলীফা’, তখন শব্দটি উহার আভিধানিক অর্থে (স্থালাভিষিক্ত)ব্যবহৃত হইয়াছিল এবং লোকদিগকে পরিস্কার ভাষায় জানাইয়া দেওয়া হইয়াছিল যে, রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনে রাসূলে করীম(সা)-এর স্থলাভিষিক্ত হওয়াই তাঁহার একমাত্র মর্যাদা। আভিধানিক অর্থ ছাড়া অন্য কোন অর্থে তখন এই শব্দটি ব্যবহৃত হইয়া থাকিলে উহার পরিবর্তে হযরত উমর(রা)-এর ‘আমিরুল মু’মিনীন’ শব্দ ব্যবহারে সম্মত হওয়ার কোনই কারন ছিল না।
‘আমীরুল মু’মিনীন’ পরিভাষা গ্রহনের অন্তরালে আরও একটি কারণ বিদ্যমান ছিল। ইসলামী রাষ্ট্র-ব্যবস্থা তখন সমগ্র আরব উপদ্বীপ ও অন্যান্য বিপুল বিস্তীর্ণ অঞ্চলে এক ব্যাপক বিপ্লব সৃষ্টি করিয়াছিল। এই বিপ্লবের গতি যেমন ছিল তীব্র,তেমনি ব্যাপক ও সর্বাত্মক।সমগ্র পৃথিবীর মানুষ সে বিপ্লবের রূপ দর্শনে বিস্ময়-বিমুগ্ধ ও হতবাক হইয়াছিল। কিন্তু আল্লাহ্র কিতাব ও রাসূলের সুন্নাতে এই পর্যায়ে কেবলমাত্র কতকগুলি মূলনীতিই দেওয়া হইয়াছিল,বিস্তারিত ও খুঁটিনাটি বিধান তাহাতে ছিল না। অবশ্য কুরআনে শু’রা- পারস্পরিক পরামর্শ গ্রহণকে রাষ্ট্র-ব্যবস্থার মৌল ভিত্তি ও বাস্তব কর্মপন্থারূপে ঘোষিত হইয়াছে।আল্লাহ্ তা’আলা রাসূলে করীম(স) কে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া দিয়াছেনঃ*******(আরবী) ‘হে নবী, জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় যাবতীয় ব্যাপারে লোকদের সহিত পরামর্শ কর’। মুসলমানদের আচরণ পদ্ধতি ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ও একস্থানে বলা হইয়াছে,******(আরবী) তাহাদের যাবতীয় জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় কাজকর্ম পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে সুসম্পন্ন হইয়া থাকে’।
এই দৃষ্টিতে খিলাফতে রাশেদার প্রত্যেক খলীফাকে যাবতীয় জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ কার্যাদি কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে ও ভিত্তিতে পারস্পরিক পরামর্শক্রমে সম্পন্ন করিতে হইত।এই কারণে তাঁহাদের মর্যাদা এক-একজন সেনাধ্যক্ষ হইতে ভিন্নতর কিছু ছিল না। সেনাধ্যক্ষ যুদ্ধসংক্রান্ত যাবতীয় কাজের ব্যাপারে মৌল হেদায়েত ও নির্দেশ মূল ক্ষমতাধর ব্যক্তির নিকট হইতেই লাভ করিয়া থাকে।কিন্তু যুদ্ধকালীন সৈন্য পরিচালনা(Operation) ও যুদ্ধ ময়দানের ক্রিয়াকলাপ ইত্যাদি সবকিছুই সেনাধ্যক্ষকে নিজেকেই এবং নিজের একক দায়িত্বেই সম্পন্ন করিতে হয়। খিলাফতে রাশেদাকেও রাষ্ট্র ও দেশ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য সমসাময়িক পরিস্থিতি অনুযায়ী শরীয়াতের সীমার মধ্যে থাকিয়া ও রাসূলে করীম(সা)-এর আদর্শ সম্মুখে উদ্ভাসিত রাখিয়া আদর্শবাদী জননেতাদের পরামর্শক্রমে নিজেকেই আঞ্জাম দিতে হইত।প্রথম খলীফা কোন ব্যাপারে বিদ্যমান পরিস্থিতির আলোকে কোন বিশেষ কর্মনীতি গ্রহন করিয়া থাকিলে দ্বিতীয়,তৃতীয় বা চতুর্থ খলীফাকে ও হুবহু ঠিক সেই কর্মনীতিই গ্রহন করিতে হইবে-অবস্থা ও পরিবেশ পরিস্থিতি যতই পরিবর্তিত হউক না কেন-এমন কোন বাধ্যবাধকতা অবশ্যই ছিল না। এই কারণেই দ্বিতীয় খলীফা ‘খলীফায়ে রাসূল’ ইত্যাদি ধরনের উপাধি গ্রহনের পরিবর্তে সম্পূর্ণ নূতন এবং দায়িত্ব ও পদমর্যাদা সহিত পুরাপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ উপাধি ‘আমিরুল মু’মিনীন’ গ্রহন করাই সমীচীন মনে করিয়াছিলেন।
হযরত আবূ বকর (রা) তাঁহার খিলাফত আমলের অত্যল্প সময়ের মধ্য সমগ্র আরব দেশে যে বিপ্লবের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, উহার প্রতি পর্যবেক্ষকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপে একথা স্পষ্ট হইয়া উঠে যে, নম্রতা, কোমলতা ও ক্ষমতাশীলতা এবং কঠোরতা ও অনমনীয়তার ক্ষেত্র ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে এবং কঠোরতার স্থানে কঠোরতা ও অনমনীয়তার ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে এবং কঠোরতার স্থানে কঠোরতা ও নম্রতা-নমনীয়তার স্থানে নম্রতা-নমনীয়তা অবলম্বিত না হইলে রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় পর্যায়ের কোন কাজই সুষ্ঠু ও যথার্থরূপে সম্পন্ন হইতে পারে না। শুধু হযরত আবূ বকর(রা)ই নহেন, পরবর্তী তিনজন খলীফার সাফল্য ও অসাধারণ শক্তি-সামর্থের পশ্চাতেও এ নিগূঢ় তত্ত্বই নিহিত যে, তাঁহারা অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সঠিক ও নির্ভুল পদক্ষেপ গ্রহনে সম্পূর্ণ সক্ষম ছিলেন।
সমসাময়িক আরবের রাজনৈতিক ব্যবস্থা
রাসূলে করীম (স)-এর সময় আরবদেশ অসংখ্য প্রকারের ধর্মমতের লীলাক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল।উহার উত্তর-দক্ষিণ অংশ পরস্পর হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ছিল। একাংশের অধিবাসীদের কোন সম্পর্ক অপরাংশের জনগণের সহিত ছিল না। উভয় অংশের লোকদের সাধারণ অবস্থাও কিছুমাত্র অভিন্ন ছিল না। ইয়েমেন ইরানীদের কর্তৃত্বাধীন ছিল। খৃষ্টধর্ম ও মূর্তি পূজার ধর্ম সেখানে পাশাপাশি চলিতে ছিল। তাহাদের হেমায়ারী ভাষা কুরাইশদের ভাষা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্নতর ছিল। উপরন্তু ইয়েমেন ছিল কয়েক শতাব্দী কাল ধরিয়া সভ্যতা ও সংস্কৃতি পাদপীঠ। পক্ষান্তরে হিজাজের লোকেরা ছিল অসভ্যতা ও যাযাবরত্তের প্রতীক।এই অঞ্চলে মক্কা,ইয়াসরীব(মদীনা) ও তায়েফ-মাত্র এই তিনটি স্থান ছিল ‘শহর’ নামে অভিহিত হওয়ার যোগ্য। আর হিজাজের বিশাল অঞ্চলের মধ্যে অবস্থান ছাড়া এই তিনটি শহরের মধ্যে পারস্পরিক কোন সম্পর্ক বা সাদৃশ্য ছিল না। অবশ্য এই শহরত্রয়ের লোকদের মধ্য আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপিত ছিল। কিন্তু এই তিনটি শহরের প্রশাসন ব্যবস্থা ছিল সম্পূর্ণ গোত্রবাদ ভিত্তিক এবং পরস্পরক বিচ্ছিন্ন। মক্কায় মূর্তি পূজার প্রাবল্য ও ব্যাপকতার সঙ্গে সঙ্গে খৃস্টবাদেরও আনুকূল্য ছিল। মদীনায় ইয়াহুদী গোত্রসমূহ বাহ্যতঃ পরাক্রমশালী হইলেও মূর্তি পূজারীদের সংখ্যা ছিল গরিষ্ঠ। এই বিশাল আরব উপদ্বীপে যখন তাওহীদের বাণী ধ্বনিত হইল এবং আল্লাহ্ তা’আলা আরবের চতুর্দিকে দ্বীন-ইসলামকে প্রসারিত করিতে চাহিলেন, তখন তিনি উহার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাও সম্পূর্ণ করিয়া দিলেন। ইয়েমেন পারসিকদের দাসত্ব হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিল।তৎসঙ্গে সমস্ত বৈদেশিক প্রভাব-প্রতিপত্তি হইতেও তাহারা সম্পূর্ণ মুক্ত হইয়া গেল।মক্কা বিজয়ের পর সমগ্র আরবদেশে ইসলাম তীব্র গতিতে প্রচারিত হইতে লাগিল।হিজাজের পর অন্যান্য আরব অঞ্চলেও ইসলাম প্লাবনের মতই বিস্তার লাভ করিল।এইভাবে অতি অল্প সময়ের মধ্যে সমগ্র আরব উপদ্বীপ ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় লাভে ধন্য হইল। এই বিশাল অঞ্চলের সমস্ত জনতা একই আদর্শে দীক্ষিত হইয়া গেল।রাসূলে করীম(স)-এর প্রতি ঈমান এবং তাঁহার প্রচারিত দিন-ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসাবে গ্রহণের ব্যাপারে সমগ্র আরব অভিন্ন ও ঐক্যবদ্ধ হইয়া উঠিলেও প্রতিটি গোত্র নিজ নিজ স্থানে সম্পূর্ণ স্বাধীন ও সার্বভৌম মর্যাদায় অভিষিক্ত ছিল। অবশ্য ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ ‘রুকন’-যাকাত-মদীনার রাজধানীতে পাঠাইতে সব অঞ্চলের লোকেরাই সমানভাবে বাধ্য ছিল।
দ্বীন ও ধর্মের ঐক্য ও একত্ব আরবদের রাষ্ট্র ব্যবস্থায় বিপ্লব সৃষ্টির হিসেবে কাজ করিয়াছে।মদীনার চতুর্দিকে বসবাসকারী গোত্রসমূহ রাসূলে করিম(স)-এর সহিত মিত্রতার চুক্তি সম্পন্ন করিয়া লইয়াছিল।তিনি যখন মক্কা বিজয়ের অভিযানে যাত্রা করিলেন,তখন এইসব গোত্র চুক্তি অনুযায়ী কাফেলার সহিত শামিল হইয়াছিল।মক্কা বিজয়ের পর সেখানকার গোত্রসমূহ সাগ্রহে ইসলাম গ্রহন করিল।অতঃপর তাহারাও ইসলামের বিজয় অভিযানসমূহে যোগদানের ইচ্ছা প্রকাশ করিল।হুনাইন ও তায়েফ যুদ্ধে ইহারা যথারীতি অংশ গ্রহন করে। এইভাবে ইসলাম যখন চতুর্দিকে বিস্তার লাভ করিল, তখন নবী করীম(স) আরব গোত্রসমূহের লোকদিগকে কুরআন মজীদ ও দ্বীনী বিষয়াদি শিক্ষা দানের জন্য লোক নিযুক্ত করিয়া চতুর্দিকে পাঠাইয়া দিলেন।কুরআন শরীফ ও দ্বীন-ইসলাম শিক্ষাদানের সঙ্গে সঙ্গে যাকাত আদায়ের দায়িত্বও কর্মচারীদের উপর ন্যস্ত করা হইল।অত্যল্প সময়ে সৃষ্ট এই দ্বীনী বিপ্লবের প্রভাবে সমগ্র অঞ্চলে রাজনৈতিক বিপ্লব সৃষ্টিও অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল।দ্বীন ও ধর্মের দিক দিয়া সমগ্র আরব এক ও অভিন্ন হইয়া উঠার পর রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক দিক দিয়াও এক অভিন্ন সত্তা ও সংস্থায় পরিণত হওয়া ছিল অত্যন্ত স্বাভাবিক পরিণতি। কিন্তু আরব বেদুঈনরা এই ধরনের রাজনৈতিক বিপ্লবের সহিত কিছুমাত্র পরিচিত ছিলনা। রাসূলে করীম(স)-এর অন্তর্ধানের পর তাঁহার স্থলাভিষিক্তেরও অনুরুপভাবে আনুগত্য স্বীকার করিতে হইবে,ইহা ছিল তাহাদের চিন্তা-ভাবনার অতীত।তাহার মনে করিত,রাসূলে করীম (স) উপস্থাপিত শিক্ষা,দ্বীন ও আদর্শ তো তাহাদের মন-মগজ ও জীবনে দৃঢ়মূল হইয়া বসিয়া আছে। ইসলামের পূর্নাঙ্গ বিধান তো তাহারা পালন করিয়া চলিবেই। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও রাজনৈতিক দিক দিয়া তাহারা হইবে সম্পূর্ণ স্বাধীন।প্রতিটি গোত্রই পূর্বের ন্যায় বাহিরের রাষ্ট্র ও সরকারের সর্ব প্রকার প্রভাব হইতে থাকিবে সম্পূর্ণ মুক্ত ও বন্ধনহীন।
বস্তুতঃরাসূলে করীম (স)-এর অন্তর্ধানের পর আরব উপদ্বীপের দিকে দিকে যে বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলিত হয়, তাহার মূলে ছিল স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতার এই অনমনীয় ভাবাধারারই প্রাবল্য। অধিকাংশ আরব গোত্রেরই অবস্থা ছিল এইরূপ। কিন্তু প্রথম খলীফা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) চাহিয়াছিলেন, আরব গোত্রসমূহ রাসূলে করীম (স)-এর জীবদ্দশায় যেরূপ ইসলামী রাষ্ট্রের অধীন হইয়াছিল, সেই অবস্থার বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হইতে দেওয়া হইবে না। কিন্তু আরব গোত্রসমূহ তাহাদের হৃত রাজনৈতিক স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার হইবে বলিয়া মনে-প্রাণে আশা করিয়াছিল। হযরত আবূ বকর (রা) তাঁহার সাচ্চা ঈমানী শক্তির বলে বলিয়ান হইয়া আপন সংকল্পে অবিচল থাকিলেন।মুসলমান হিসাবে প্রত্যেক স্ব স্ব দায়িত্ব পালন করুক এবং ইসলামের উপস্থাপিত ঐক্য ও সংহতির আদর্শ সকলেই পুরোপুরি মানিয়া চলুক, ইহাই ছিল তাঁহার আন্তরিক বাসনা।তিনি স্পষ্টতঃজানাইয়া দিলেন যে, রাসূলের জীবনকালে যাকাত, ওশর ও খারাজ বাবদ যে সম্পদ মদীনায় প্রেরিত হইত, তাহা অবশ্যই আদায় করিতে হইবে। কিন্তু আরব গোত্রসমূহ সেজন্য প্রস্তুত হইতে পারিতে ছিল না। তাহারা স্পষ্ট ভাষায় বলিতে শুরু করিল, রাসূলে করীম (স)-এর ব্যাপারে ছিল সম্পূর্ণ ভিন্নতর।তিনি আল্লাহ্র রাসূল ছিলেন।তাঁহার প্রতি অহী নাযিল হইত। তাঁহার পুর্ণাঙ্গ আনুগত্য স্বীকার করা মুসলিম মাত্রেই কর্তব্য ছিল। কিন্তু এখন অবস্থার পরিবর্তন হইয়াছে। এখন তদনুসারে রাষ্ট্র ব্যবস্থায়ও পরিবর্তন আনিতে হইবে। কিন্তু এই চিন্তা ও মানসিকতা কোনক্রমেই ইসলামী রাষ্ট্র সংস্থা গড়িয়া উঠার অনুকূল ছিল না।হযরত আবূ বকর (রা)প্রবল শক্তিতে এই নৈরাজ্যমূলক মানসিকতা নির্মূল করিয়া দিলেন।এই পর্যায়ে তিনি যে গভীর বিচক্ষণতাপূর্ণ ও বুদ্ধিসম্মত পন্থা গ্রহন করিয়াছিলেন, তাঁহার ফলে সমগ্র আরবদেশ একটি অভিন্ন রাষ্ট্র-সংস্থার অধীনে সুসংগঠিত ও সুসংবদ্ধ হইয়া উঠিল।তিনি দেশ শাসন,রাষ্ট্র পরিচালনা ও যুদ্ধ-সন্ধির ব্যাপারে সমগ্র গোত্রসমূহকে ঐক্যবদ্ধ করিয়া লইলেন। সকল পর্যায়ের লোকদের সহিত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে পরামর্শ গ্রহণের নীতি কার্যকর করিলেন। ফলে সকল গোত্রই নিজদিগকে ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনায় সমান অংশীদার মনে করিতে শুরু করিল।প্রতিটি ব্যক্তি ও গোত্র সর্বক্ষেত্রে সমান গুরুত্ব, মর্যাদা ও অধিকার লাভ করিতে পারিয়া বিপুল উৎসাহ –উদ্দিপনা সহকারে রাষ্ট্র-সংস্থার আনুগত্যে নিজেদের সোপর্দ করিল।খলীফাই ছিলেন এই আনুগত্যের কেন্দ্রীয় ব্যক্তি সত্তা। তাঁহার যে কোন আদেশ ও নিষেধ পালনতাহাদের জন্য অবশ্য কর্তব্য,এই ব্যাপারে তাহাদের মধ্যে আর কোন মতদ্বৈততা থাকিল না।
খিলাফতের রাষ্ট্র-রূপ
ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার আদর্শিক পরিচিতি কি?উহা কোন্ ধরনের রাষ্ট্র ব্যবস্থা? উহা কি নিরেট থিওক্রাসী(Theocracy), যেখানে কোন আল্লাহ্প্রিয় ব্যক্তি স্বয়ং কিংবা যাজক সম্প্রদায় শাসন কার্য পরিচালনা করেন? কিংবা উহা আধুনিক পরিভাষা অনুযায়ী একটি গণতান্ত্রিক(Democrative) অথবা কোন স্বৈরতান্ত্রিক(Autocracy) শাসন? কিংবা উহা এক ধরনের রাজতন্ত্র? এই প্রশ্ন একালের বহু চিন্তাবিদকে পর্যন্ত বিভ্রান্ত করিয়াছে। কিন্তু ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞানও যাঁহাদের আছে, তাঁহারা এই ধরনের প্রশ্নে কিছুমাত্র বিচলিত হইতে পারেন না। কেননা খিলাফত যে কোনক্রমেই পোপতন্ত্র বা থিওক্রাসী ধরনের শাসন ব্যবস্থা নয়, তাহা বুঝিবার জন্য বিশেষ পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন হয় না। প্রাচীন কালের ফিরাউন কিংবা আধুনিক ইউরোপসহ দুনিয়ার অন্যান্য রাজা-বাদশাহরা যে ধরনের শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করিয়াছে ও করিতেছে, খিলাফতের শাসনব্যবস্থার সহিত উহার দূরতম সম্পর্ক বা সামান্যতম সাদৃশ্যও খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।আধুনিক ধরনের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও উহাকে বলা যাইতে পারে না- যদিও সর্বজনীন মূল্যবোধ এবং জনগণের অধিকার ও ব্যক্তি স্বাধীনতার সুযোগ-সুবিধা উহাতে ছিল পূর্ণমাত্রায় কার্যকর,যা পাশ্চাত্যের ধর্মহীন গনতন্ত্রে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।
কোন একজন খলিফাও নিজেকে আল্লাহ্ কর্তৃক মনোনীত, আল্লাহ্র সহিত বিশেষ সম্পর্কের অধিকারী কিংবা আল্লাহ্র নিকট হইতে প্রত্যক্ষ বিধান-ওহী- লাভ করার কোন দাবি কখনও করেন নাই। এইরূপ দাবি উত্থাপনকে তাঁহারা সম্পূর্ণ হারাম মনে করিতেন। কেননা প্রকৃতপক্ষেও ইহা ছিল সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। রাসূলে করীম (স)- এর ইন্তেকালের সঙ্গে সঙ্গে ওহী নাজিলের ধারা চিরতরে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। অতঃপর দুনিয়ার মানুষের নিকট জীবন, সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য মাত্র দুইটি ভিত্তিই অবশিষ্ট রহিয়াছে। একটি আল্লাহ্র কিতাব আর দ্বিতীয়ত রাসূলের সুন্নাত। আল্লাহ্ তা’আলা বিশ্ব মানবের জন্য সার্বিক ও পূর্ণাঙ্গ বিধান হিসেবে সর্বশেষ নবীর মাধ্যমে কুরআন মজীদ নাজিল করিয়াছেন। আর রাসূলে করীম (স) আল্লাহ্র সেই বিধানকে দৈনন্দিন কাজের মাধ্যমে বাস্তবায়িত করিয়াছেন। কুরআন অনুযায়ী রাসূলে করীম (স)-এর কাজ কুরানেরই বাস্তব ব্যাখ্যা। এই ব্যাখ্যা কুরানের ন্যায় চিরন্তন ও চির অনুসৃতব্য। খলীফা বা রাষ্ট্র চালক এই দুইটি বিধান অনুসরন করিয়া চলিতে বাধ্য। ইহাদের নির্ধারিত সীমা একবিন্দু লংঘন করার অধিকার কাহারও নাই। সাধারণ মানুষ একজন রাষ্ট্র চালককে মানিয়া চলিতে বাধ্য কেবলমাত্র এইজন্য যে, এই আনুগত্য রাষ্ট্র চালকের নিজস্ব গুণ বা অধিকারের জন্য নয়। ব্যক্তিগত গুণ-মর্যাদা বা অধিকারের কারণে কোন লোকই কাহাকেও মানিয়া চলিতে বাধ্য নয়। সে যদি আল্লাহ্র বিধান ও রাসূলের সুন্নাত অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা করে- আইন প্রণয়ন ও কার্যকর করে, তবে কেবলমাত্র এইজন্যই তাহাকে মানিয়া লইতে সকলে বাধ্য। কেননা এই আনুগত্য মূলত আলাহর আনুগত্য-আল্লাহ্র বিধান পালনের মাধ্যমে।প্রসঙ্গত স্মর্তব্য যে, আল্লাহ্র বিধান ও রাসূলের সুন্নাতের ব্যাখ্যাদানের একচেটিয়া অধিকার কাহারও নাই-এমন কি খলিফারও নয়। কুরআন-সুন্নাহর পারদর্শী যে কোন লোক উহা ব্যাখ্যাদানের অধিকারী। খলীফার এমন কোন ব্যাখ্যাও মানিয়া লওয়া যাইতে পারে না, যাহা আজ পর্যন্ত অন্য কোন বিশেষজ্ঞ কর্তৃকই স্বীকৃত হয় নাই। কাজেই কুরআন ও সুন্নাহর নামে নিজের মনগড়া বিধান চালু করা ইসলামী রাষ্ট্রশাসকের পক্ষে কোনক্রমেই সম্ভব হইতে পারে না। কেননা উহার অমূলকত্ত ও ভিত্তিহীনতা গোপন করার সাধ্য কাহারো নাই। খলীফার কুরআন-সুন্নাহ পরিপন্থী কোন নির্দেশ পালন করিতে কোন লোকই বাধ্য নয়। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক(রা)-এর উপরোদ্ধৃত ভাষণসমূহে এই কথাই উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষিত হইয়াছে। পরবর্তী খলিফাগণও নিজ নিজ ভাষায় এই কথার প্রতিধ্বনি বারবার করিয়াছে।
ইসলাম নির্ধারিত এই কর্মনীতি ও রাষ্ট্র শাসন পদ্ধতি পোপতন্ত্র তো নয়ই,ইহা গনতন্ত্র, রাজতন্ত্র বা স্বৈরতন্ত্রও নয়। কেননা পোপতন্ত্রে পাদ্রি-পুরোহিতরা আল্লাহ্র নামে নিজেদের মনগড়া শাসন চালায়। সে সম্পর্কে অন্য কাহারও কোন মন্তব্য করার অধিকার নাই। রাজতন্ত্র ও স্বৈরতন্ত্রে তো জনসাধারণ সকল প্রকার মানবিক ও মৌলিক অধিকার হইতেই সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত থাকিতে বাধ্য হয়। আর তথাকথিত গনতন্ত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে চলে দল-প্রধান বা দলের প্রভাবশালী লোকদের অথবা ক্ষমতা দখলকারী মুষ্টিমেয় কোটারীর চরম স্বেচ্ছাচারিতা। ইসলামী খিলাফতে আল্লাহ্র বিধান ও রাসূলের সুন্নাত মানিয়া চলার ব্যাপারে শাসক ও শাসিত, খলীফা ও জনগন সকলেই সমানভাবে বাধ্য;বরং যে ব্যক্তি এই মান্যতার দিক দিয়া অন্যদের তুলনায় অধিক অগ্রসর,সে-ই হয় এই রাষ্ট্রের খলীফা। খিলাফতের পদে নিযুক্ত হইয়া কোন ব্যক্তি কুরআন-সুন্নাহর বিধানও নিজ ইচ্চামত জারী করিতে পারে না। সেজন্য কুরআন-সুন্নাহ্ বিশেষজ্ঞদের সহিত পরামর্শ করিতে সে বাধ্য। কিন্তু পোপতন্ত্রে ধর্মযাজকরাই নিরংকুশ ক্ষমতার মালিক। তাহারা কাহারও সহিত কোন ব্যাপারে পরামর্শ করিতে বাধ্য নয়। তাহাদের কোন সিদ্ধান্ত সম্পর্কে কেহ প্রশ্ন তুলিতে পারে না; বরং তাহাদের কার্যাবলীর বিরূপ সমালোচনা করার পরিণতি অপঘাতে মৃত্যুবরণ ছাড়া আর কিছুই নয়। সাধারণ লোক সেখানে নিকৃষ্টতম গোলামের জীবন যাপন করিতে বাধ্য। পক্ষান্তরে ইসলামী খিলাফতে প্রত্যেকটি মানুষই স্বাধীন। সেখানে সমালোচনা করার শুধু অধিকারই দেওয়া হয় নাই, উহা প্রতিটি নাগরিকের দ্বীনী কর্তব্য বলিয়াও ঘোষিত হইয়াছে।
স্মর্তব্য যে, কুরআন ও সুন্নাহ ইসলামী খিলাফতের ভিত্তি বটে;কিন্তু উহাতে কেবলমাত্র মূলনীতি পেশ করা হইয়াছে। বিস্তারিত ও খুঁটিনাটি বিষয় উল্লেখ হইতে ইচ্ছা করিয়াই বিরত থাকা হইয়াছে। কোথাও তেমন কিছু উল্লেখিত হইয়া থাকিলেও অপরিহার্য ছিল বলিয়াই তাহা করা হইয়াছে। সেখানে তাহা উল্লেখিত না হইলে কুরআন ও সুন্নাতের বাস্তবায়ন সম্ভব হইত না। ইসলামী খিলাফতের যাবতীয় কাজ সেই সব মূলনীতির ভিত্তিতে সুসম্পন্ন করা হয়। সেসব মূলনীতির ভিত্তিতে বিস্তারিত ও খুঁটিনাটি বিষয় স্থির করা সর্বসাধারণ মানুষের দায়িত্ব এবং এই ব্যাপারে কাহারও একচেটিয়া অধিকার নাই। বস্তুতঃএই কারণেই ইসলামের জীবন ও রাষ্ট্রাদর্শ চিরন্তন ও শাশ্বত মূল্য লাভ করিতে পারিয়াছে।
কুরআন ও সুন্নাহ প্রদত্ত মূলনীতিসমূহ কালজয়ী।সর্বকালে সর্বাবস্থায় এবং সর্বদেশেই উহার ভিত্তিত আদর্শ মানব সমাজ গঠন করা শুধু সম্ভব নয় অবশ্য কর্তব্যও। সে সব মূলনীতি ছাড়া আদর্শ সমাজ গঠনের স্বপ্ন কোনদিনই বাস্তবায়িত হইতে পারেনা। মুসলমান যতদিন সেসব মূলনীতির ভিত্তিতে ব্যক্তি ও সমাজ গঠন করিয়াছে এবং বাস্তবে উহা অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে, ততদিন তাহারা যে ক্রমশঃধাপে ধাপে উন্নতির দিকে ধাবিত হইয়াছে, ইতিহাসই উহার অকাট্য প্রমাণ। কিন্তু যখনি সে মূলনীতিসমূহ ব্যক্তিগত ও জাতীয় পর্যায়ে পরিত্যক্ত হইয়াছে, উহার পরিপন্থী নীতি ও আদর্শ মানিয়া চলিতে শুরু করিয়াছে,তখনি তাহাদের পতন সূচিত হইয়াছে। বর্তমান বিশ্বের মুসলমানদের বাস্তব অবস্থা ইহারই জীবন্ত সাক্ষী।
আল্লাহ্র কিতাব ও রাসূলের সুন্নাতের ব্যাখ্যাদানের একচেটিয়া অধিকার বিশেষ এক শ্রেণীকে দেওয়া হইলে ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থাও ‘থিওক্রাটিক বা যাযকতন্ত্রও’ হইয়া যাইত; কিন্তু ইসলামে যে পৌরোহিত্যবাদ নাই, বিশেষ এক শ্রেণীর কোন একচেটিয়া কর্তৃত্বও ইহাতে স্বীকৃত নয়, একথা সর্বজনবিদিত। এখানে প্রত্যেক ব্যক্তিই স্বীয় যোগ্যতা বলে কুরআন ও সুন্নাহ অধ্যয়ন, চিন্তা-গবেষণা, বিচার-বিবেচনা এবং ফলাফল ও সিদ্ধান্ত গ্রহন অধিকারী। এই ব্যাপারে নির্বিশেষে সকলেরই সমান অধিকার রহিয়াছে। -শুধু তাহাই নয়,এই অধিকার প্রয়োগ করার জন্য সর্বসাধারণকে স্পষ্ট ভাষায় নির্দেশও দান করা হইয়াছে। কাজেই ইহার সহিত পোপতন্ত্রের(Papacy) যে দূরতম সম্পর্ক বা সাদৃশ্যও নাই, তাহা বলাই বাহুল্য।
ইসলামী খিলাফতে প্রত্যেক নাগরিককে শাসন কর্তৃপক্ষের প্রকাশ্য সমালোচনার অধিকার দেওয়া হইয়াছে। তাহাদের কাজকর্মের প্রতি তীক্ষ্ণ সজাগ দৃষ্টি রাখা এবং কুরআন ও সুনাহর আলোকে কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি গোচরীভূত হইলে সঙ্গে সঙ্গে উহার প্রতিবাদ করা ও উহার প্রতিকারের জন্য বাস্তব কর্মপন্থা গ্রহণ করা প্রতিটি নাগরিকের কর্তব্য বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। এই শাসন ব্যবস্থায় রাষ্ট্র পরিচালকগন নিজেদের জন্য কোন বিশেষ আইন রচনা করিয়া কোন বিশেষ অধিকার ভোগ করার সুযোগ পাইতে পারে না।খিলাফতে রাশেদার আমলে কুরআন ও সুন্নাহর বিধান শক্তভাবে পালন করার ফলে ইসলামী সমাজ এই ধরনের যাবতীয় অবাঞ্চিত ও কলঙ্কজনক আচরণ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র রহিয়াছে।তখন জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব এবং যাবতীয় অর্থ সম্পদ ছিল এক মহান আমানত। এই আমানতে বিন্দুমাত্র খিয়ানত করিলেও কিয়ামতের দিন কঠিন শাস্তি ভোগ করিতে হইবে, এই বিশ্বাস প্রত্যেকের মনে ইস্পাতের ন্যায় দৃঢ়মূল হইয়াছিল।
খিলাফতে রাশেদার চারজন খলীফাই জাতি ও রাষ্ট্রের অর্পিত আমানতসমূহ অত্যন্ত সযত্নে রক্ষণাবেক্ষণ করিয়াছেন,সে সবের যথাযথ ব্যয়-বণ্টন ও বিনিয়োগ নিশ্চিত করিয়াছেন এবং নিঃছিদ্র একনিষ্ঠতা, ঐকান্তিকতা, নিঃস্বার্থতা ও উচ্চমানের তাকওয়া-পরহেজগারীর বাস্তব নিদর্শন উপস্থাপিত করিয়াছেন। একালের লোকদের দৃষ্টিতে তাহা আজগুবী,অস্বাভাবিক ও অকল্পনীয় মনে হইলেও খিলাফতে রাশেদার ব্যাপারে উহাই ছিল বাস্তব সত্য। বস্তুতঃখিলাফত ও নেতৃত্ব তাঁহাদের মনে ও চরিত্রে বিন্দুমাত্র বিকৃতি ঘটাইতে পারে নাই; বরং তাহাদের তাকওয়ার মান ও মাত্রা পূর্বের তুলনায় অধিক বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছে।জনগণের ধন-সম্পদ হইতে অন্যায় ফায়দা লাভ,ক্ষমতার অপব্যবহার এবং নিজ বংশ ও আত্মীয়-স্বজনের জন্য বিশেষ সুযোগ-সুবিধা বিধানের চিন্তা তাঁহাদের মনে-মগজে মুহূর্তের তরেও স্থান লাভ করিতে পারে নাই। খিলাফতের কঠিন দায়িত্ব অর্পিত হওয়ার মুহূর্ত হইতেই তাঁহারা নিজেদের ব্যক্তিসত্তা ও বংশ-পরিবারবর্গকে বেমালুম ভুলিয়া গিয়া আল্লাহ্র দ্বীনের মর্যাদা রক্ষা এবং রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় কার্যাবলী সুসম্পাদনে নিজেদের সমগ্র শক্তি নিয়োজিত করিয়া ছিলেন।সর্বক্ষেত্রে ও সর্বব্যাপারে ইনসাফ ও পরিপূর্ণ সুবিচার প্রতিষ্ঠাই ছিল তাঁহাদের কর্মব্যস্ততার চরমতম লক্ষ্য। দুর্বল ও অভাবগ্রস্ত লোকদের সাহায্য দানের তুলনায় অধিক প্রিয় ব্যস্ততা তাঁহাদের নিকট আর কিছু ছিলনা।
যে রাষ্ট্র-ব্যবস্থা এই প্রকৃতির হয়, সেখানে স্বৈরাচার ও অত্যাচার-জুলুমের নাম-চিহ্ন পর্যন্ত থাকিতে পারে না। যে-রাষ্ট্রের কর্ণধার ও দায়িত্বশীল কর্মকর্তাবৃন্দ নিজদিগকে সাধারণ লোকের ঊর্ধ্বে মনে করেন না, মনে করেন সর্বসাধারণের খাদেম,উহাকে না পোপতন্ত্র বলা যাইতে পারে, না স্বৈরতন্ত্র। আধুনিক কালের তথাকথিত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের চরিত্রের সহিতও ইহার কোন সাদৃশ্য পাওয়া যাইতে পারে না। একথা সত্য যে, বর্তমানের ন্যায় সেকালে সাধারণ বয়স্ক ভোটাধিকারের(Adult suffrage) ভিত্তিতে খলীফা চতুষ্টয় নির্বাচিত হন নাই। যে অস্থির ও অশান্তিময় পরিস্থিতিতে এক এক ব্যক্তি খলীফা পদে বরিত হইয়াছেন, তাহাতে এই ধরনের নির্বাচনের কথা কল্পনাও করা যায় না। তৎসত্ত্বেও তদানীন্তন সমাজে তাঁহারাই যে সর্বাধিক আস্থাভাজন ব্যক্তি ছিলেন এবং ঐধরনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইলে তাঁহারাই যে নির্বাচিত হইতেন,ইহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ করা যায় না।খলীফা নির্বাচনে সাধারণতঃমুহাজির ও আনসার গোত্রের লোকেরাই অংশ গ্রহন করিতেন।আরবের তৎকালীন পরিস্থিতিতে অন্যান্য গোত্রের লোকদের সহিত এ ব্যাপারে পরামর্শ গ্রহণ করারও প্রয়োজন মনে করা হইত না তবে এই নির্বাচন গোত্রীয় গোপন যোগ-সাজশেরও পরিণতি ছিল না। আনসার ও মুহাজিররা কার্যতঃতদানীন্তন আরবের প্রায় সমস্ত গোত্রের মুসলিম জনতার প্রতিনিধিস্থানীয় ছিলেন।তাঁহাদের মতই ছিল সাধারণভাবে সমস্ত আরব মুসলিম জনতার রায়। রাসূলে করিম(স)-এর কিংবা পরবর্তী খলীফাদের এক একজনের আকস্মিক অন্তর্ধানের পর যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়, প্রত্যেক খলীফার নির্বাচনের মাধ্যমে তৎকালীন জরুরী পরিস্থিতিতে, অনতিবিলম্বে সেই শূন্যতা পূরণই অপরিহার্য এবং সর্বাধিক জরুরী কাজ হইয়া দেখা দিয়াছিল মুসলিম জাতির সম্মুখে।
এতৎসত্ত্বেও প্রত্যেক খলীফাই সমাজের সাধারণ আস্থাভাজন ব্যক্তিদের সহিত পরামর্শ করিয়াই রাষ্ট্র পরিচালনা করিয়াছেন। কেহই নিজের একক ও যুক্তিহীন মতের ভিত্তিতে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারসমূহে। খলীফাদের নির্বাচনে আত্মীয়তা কিংবা বংশমর্যাদা কোন কার্য-কারণ(Factor) হইয়া দেখা দিতে পারে নাই। তাঁহাদের কেহই এই পদের জন্য প্রার্থী হন নাই। এই পকদে নিযুক্ত হওয়ার লক্ষ্যে তাঁহাদের কেহ জনমত অনুকূলে আনার কোন অভিযান চালানোর আত্মনিয়োগ করেন নাই; বরং প্রত্যেকই নিজের পরিবর্তে অন্য কোন যোগ্যতর ব্যক্তিকে নির্বাচিত করাইবার জন্য চেষ্টা চালাইয়াছেন। এই পর্যায়ে প্রথম খলীফার নির্বাচন-কালীন কথাবার্তা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় চিরদিন উজ্জ্বল হইয়া থাকার অধিকারী। কোন কোন খলীফার নির্বাচনে প্রথম দিক দিয়া কিছুটা মত-বিরোধ দেখা দিলেও উত্তরকালে সেই মতবিরোধ বা বিরুদ্ধতার কোন অস্তিত্ব দেখা যায় নাই; বরং সকলেই অন্তর দিয়া সে নির্বাচনকে মানিয়া লইয়াছেন এবং নির্বাচিত খলীফার সহিত আন্তরিক সহযোগিতা করিয়াছেন। ইসলামী নির্বাচন নীতির এই বৈশিষ্ট্য তুলনাহীন।এই সমাজে স্থায়ী সরকারপক্ষ এবং স্থায়ী বিরোধীদল(Opposition) বলিতে কিছুই ছিলনা। এখানে সকলেই মিলিতভাবে ন্যায় ও সত্যের সমর্থক ও সহযোগিতাকারী এবং সকলেই অন্যায় ও ভুলনীতির বিরোধী, প্রতিবাদকারী। খলিফাগণ জনগণের অধিকার ও রাষ্ট্রের কল্যাণে পারস্পরিক পরামর্শের গুরুত্ব কত বেশি স্বীকার করিতেন, প্রথম খলীফার প্রাথমিক ভাষণের নিম্নোদ্ধৃত কথাগুলি হইতেই তাহা সুস্পষ্ট হইয়া উঠেঃ
আমি তোমাদের শাসক নিযুক্ত হইয়াছি, কিন্তু আমি তো তোমাদের তুলনায় উত্তম নহি। আমি যদি ন্যায়পথে চলি, তাহা হইলে আমার আনুগত্য ও অনুসরণ করিবে। কিন্তু ন্যায়ের পথ হইতে যদি আমার পদস্থলন হয় ও অন্যায় পথে চলিতে শুরু করি, তাহা হইলে তোমারা আমাকে ঠিক করিয়া দিবে, সঠিক পথে চালাইবে। আমি যত দিন আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের আনুগত্য করিতে থাকিব, ততদিন তোমারাও আমার আনুগত্য করিতে থাকিবে;কিন্তু আমিই যদি আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের নাফরমানী করি, তাহা হইলে আমার আনুগত্য করা তোমাদের কর্তব্য নয়।
শাসকের সহিত জনগণের গভীর ও নিবিড় সম্পর্ক এবং শাসককে সঠিক পথে পরিচালন ও সমালোচনার অধিকারের এইরূপ উদার-উদাত্ত স্বীকৃতির কোন দৃষ্টান্ত বর্তমান গনতন্ত্রবাদী যুগের তথাকথিত রাষ্ট্রসমূহের কোথাও দেখা যায় কি?খিলাফতে রাশেদার গোটা শাসন-কালই ছিল আধুনিক ভাষায় বলিতে গেলে নিতান্তই জরুরী অবস্থার যুগ(Emergency Period)ছিল। কিন্তু এই দীর্ঘ সময়ে জনগণের মৌলিক অধিকার কখনোই হরণ করা হয় নাই। শু’রা-পরামর্শ গ্রহণ ব্যবস্থা-সব সময়ই সুষ্ঠু রূপে কার্যকর রহিয়াছে। শু’রা-পার্লামেন্ট-ভাঙ্গিয়া দিয়া বিশেষ ক্ষমতা(Special power)নিজ হাতে গ্রহণ করার অধিকার খিলাফতের ভিত্তি –কুরআন ও সুন্নাহ-কাহাকেও কোন অবস্থায়ই দেয় নাই।
খলিফাগনের দৃষ্টিতে সব মুসলমানই ছিল সমান অধিকার ও সমান মর্যাদাসম্পন্ন;বৈষয়িক মান-মর্যাদার কারণে কেহই অন্যদের উপর প্রাধান্য ও অগ্রাধিকার লাভ করিতে পারিত না। প্রাক্তন মুর্তাদদের সম্পর্কে প্রথম খলীফা প্রথমে এই নির্দেশ জারী করিয়াছিলেন যে, সামরিক অভিযানসমূহে তাহাদিগকে যোগদান করিতে দেওয়া যাইবে না। কেননা তখনও তাহাদের ব্যাপারে পূর্ণ আস্থা ও নিশ্চিন্ততা লাভ করা যায় নাই। কিন্তু তাহাদের সম্পর্কে সন্দেহ ও সংশয় দূরীভূত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগকে ইসলামী মুজাহিদ বাহিনীর মধ্যে শামিল হওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়। ইরান অভিযানে তাহাদেরকে কাজে লাইগাবার জন্য হযরত উমর ফারুক(রা) কে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। ইহা খিলাফতে রাশেদার উদার,নীতিনিষ্ঠ ও বিদ্বেষমুক্ত দৃষ্টিকোণের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ছাড়া আর কিছুই নয়।
আরবের রাজনৈতিক একত্ব
প্রথম খলীফা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) তাঁহার অন্যান্য বিচক্ষণতা ও দূরদৃষ্টির সাহায্যে ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার ভিত্তিকে সুদৃঢ় করিয়া তোলেন। ইহার ফলে পরবর্তী খলিফাগণের পক্ষে সেই ভিত্তির উপর একটি বিশাল রাষ্ট্রপ্রাসাদ নির্মাণ করা এবং সমগ্র আরব উপদ্বীপকে একটি মাত্র রাজনৈতিক এককে(Unit) পরিণত করা খুবই সহজসাধ্য হয়। হযরত আবূ বকর (রা)-এর ক্ষমা,সহিষ্ণুতা ও ত্যাগ-তীতিক্ষামূলক নীতির দরুণ সমগ্র আরব উপদ্বীপকে ঐক্যবদ্ধ করার পথ সুগম হইয়াছিল। প্রথম দিকের সাময়িক বিশৃঙ্খলা প্রশমিত হওয়ার পর বিদ্রোহী-অপরাধী লোকেরা তাঁহার নিকট ক্ষমা লাভ করিয়া আন্তরিকতা সহকারে খিলাফতের আনুগত্য স্বীকার করে। শু’রা ব্যবস্থা সারাদেশের রাজনৈতিক ঐক্য ও সংহতিকে অধিকতর দৃঢ় ও শক্তিশালী করিয়া তোলে। ইহারই ফলে ইরাক ও সিরিয়া বিজয় সহজতর হইয়া যায়।
এই সময়কার আরব জনগণের চিন্তা-চেতনা ও মননশীলতা শু’রা ও গণ- অধিকারসম্পন্ন রাষ্ট্র ব্যবস্থার অনুকুল হইয়াছিল। ইসলামের অভ্যুদয় ও প্রকাশ আরব দেশে ঘটিয়াছিল। ইসলামী শরীয়াত-কুরআন ও সুন্নাহ-আরবী ভাষায় সন্নিবেশিত ছিল। সর্বশেষ রাসূল আরব দেশে প্রেরিত হইয়াছিলেন। আরব-গোত্রসমূহ বেদুঈন কিংবা নগরবাসী যাহাই হউক না কেন,স্বাধীনতা ও স্বরাজের জন্য ছিল অধীর ব্যাকুল। তাহাদের নিকট ইহাপেক্ষা অধিক প্রিয় ও আকর্ষণীয় জিনিস আর কিছুই ছিল না। মরুচারীদের মধ্যে সাম্য ও সমতার ভাবধারা পুরাপুরি সংক্রমিত হইয়াছিল। ইসলামী শিক্ষা ও প্রশিক্ষন এই ভাবধারাকে অধিক স্বচ্ছতা ও পরিপক্কতা দান করে। কেননা ইসলামই প্রকৃত সাম্য ও সমতার পূর্ণাঙ্গ আদর্শ উপস্থাপন করিয়াছে। কুরআন মজীদ এই সাম্য ও সমতার বাণী উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছে। কুরআনের ঘোষণানুযায়ী বংশ মর্যাদা বা ধন-সম্পদের আধিক্য ও প্রাচুর্যের নয়, আল্লাহ্র ভয় (তাকওয়া) ও আল্লাহ্র দ্বীন পালনই মর্যাদা ও সম্মানের মানদণ্ড। বর্তমান যুগে সর্বত্র গণতন্ত্রের জয়ধ্বনি উচ্চারিত। কিন্তু প্রকৃত মানবিক মূল্যবোধ ও ভাবধারা খিলাফতে রাশেদার আমলেই সমুজ্জ্বল প্রতিভাত হইয়াছে। মানবতা, ভ্রাতৃত্ব,প্রেম-প্রীতি,স্বাধীনতা ও সাম্য বর্তমান গণতন্ত্রের স্ফীত কণ্ঠে সমুচ্চারিত। কিন্তু ইহার প্রকৃত বাস্তবায়ন কেবলমাত্র খিলাফতে রাশেদার আমলের প্রতিটি ক্ষেত্রেই দ্রষ্টব্য। ইসলামের পবিত্র শিক্ষা প্রতিটি মু’মিনকে অপর মু’মিনের একনিষ্ঠ ‘ভাই’ ও সত্যিকার কল্যাণকামী বানাইয়া দিয়াছিল। কোন লোক নিজের জন্য যাহা পছন্দ করে, অপর ভাইয়ের জন্য তাহাই পছন্দ না করা পর্যন্ত ঈমানদার হইতে পারে না-রাসূলে করীম(স)-এর ঘোষণা একটা সাধারণ ও মূল্যহীন কণ্ঠধ্বনি ছিল না। ইহা ছিল মানবাধিকারের সপক্ষে এক ঐতিহাসিক ঘোষণা। এই গভীর বুদ্ধিসম্মত ঘোষণাকে বাস্তবায়িত করিয়া তোলা না হইলে কোন রাষ্ট্রই প্রকৃত জনকল্যাণমুখী চরিত্র লাভ করিতে পারে না এবং এই ঘোষণাকে আলোক-মশালরূপে গ্রহণ করিয়া সাধারণ জনগণকে পরস্পরের কল্যাণকামী ও সহানুভূতিশীল রূপে গড়িয়া না তোলা পর্যন্ত কোন গণকল্যাণকামী রাষ্ট্রের পক্ষে বিন্দুমাত্র সাফল্য লাভ অসম্ভব। বস্তুতঃবর্তমান গণতন্ত্রবাদী রাষ্ট্রসমূহের চরম হাস্যকর ব্যর্থতা এবং খিলাফতে রাশেদার পূর্ণ সাফল্যের মূলে এই তত্ত্বই নিহিত। বলা নিষ্প্রয়োজন, রাসূলে করীম(স)-এর এবম্বিধ মহামূল্য বাণীসমূহকে ভিত্তি করিয়াই ইসলামই রাষ্ট্রের বিরাট প্রাসাদ রচনা করা হযরত আবূ বকর (রা)-এর পক্ষে সম্ভবপর হইয়াছিল। আর এই বানীসমূহের পূর্ণ অনুসরণের মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালনা করিয়া সমকালীন বিশ্বরাষ্ট্র-দর্শনের সম্পূর্ণ বিপরীত-খিলাফতে রাশেদার মহান ব্যবস্থা পরিচালনা করিয়া সমগ্র বিশ্বকে বিস্মিত-বিমুগ্ধ করা পরবর্তী খলিফাত্রয়ের পক্ষে সম্ভবপর হইয়াছিল।
ইসলামী রাষ্ট্র-নীতির অন্তর্নিহিত শক্তি
খিলাফতে রাশেদার রাষ্ট্র-ব্যবস্থা কেবলমাত্র আরব উপদ্বীপ নামক ভূখণ্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ হইয়া থাকে নাই। উহা সে ভূ-খণ্ডের সীমা অতিক্রম করিয়া অত্যল্প কালের মধ্যেই বাঁধ-ভাঙা বন্যার মত চতুর্দিকের দূর দূর-অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত ও সম্প্রসারিত হইয়া পড়ে। কিন্তু একটি আরব রাষ্ট্রের পক্ষে বিশাল অনারব এলাকায় সম্প্রসারিত হওয়া কি নিছক কতিপয় সামরিক অভিযানের পরিণতি ছিল? ইতিহাসের ইহা একটি জটিল প্রশ্ন। এই প্রশ্নের জবাব বিশ্লেষণ একান্তই আবশ্যক।
বস্তুতঃ ইসলাম এক সর্বজনীন বিপ্লবী বাণী লইয়া দুনিয়ার বুকে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। সে বানীর ব্যাপক প্রচার ও প্রসার এবং উহার অনুকূলে নীরব জনমত গড়িয়া উঠাই ইসলামের জয়জয়কার ও দেশের পর দেশ ইসলামের পতাকাতলে আশ্রয় লওয়ার এক বিস্ময়কর ইতিহাস সৃষ্টি করিয়াছে। এই বিজয়সমূহকে বৃক্ষের বৃন্ত-সংলগ্ন পাকা ফল এক টোকায় পাড়িয়া লওয়া কিংবা সদ্য-ভূমিষ্ঠ সন্তানের নাড়ি কাটিয়া দেওয়ার সহিত তুলনীয়। ইসলামী আদর্শবাদ প্রথমে ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়াছে, পথ সুগম করিয়া লইয়াছে এবং পরিণামে ইসলামী বিপ্লব সৃষ্টির সব বাধা-প্রতিবন্ধকতা দূর হইয়া গিয়াছে। এই ভাবেই মুসলমানদের পক্ষে দুনিয়ার বিশাল অঞ্চলে ইসলামী রাষ্ট্রকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর গড়িয়া তোলা সম্ভবপর হইয়াছিল।
ইসলামী ইতিহাসের প্রাথমিক পর্যায় সম্পর্কে অবহিত কোন ব্যক্তির নিকটই একথা গোপন থাকিতে পারে না যে, ইসলামের মুজাহিদদের সাফল্য কোন সাময়িক বা দুর্ঘটনামূলক ব্যাপার ছিল না। এই বিজয় ছিল ঘটনা-প্রবাহের এক দীর্ঘ ধারাবাহিকতার অবিচ্ছিন্ন অংশ। মূলতঃ ইসলাম দুনিয়ায় যে বিপ্লব সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহা ছিল অবধারিত। কেননা ইসলামের মূল আদর্শেই বিপ্লবের অগ্নিবাস্প নিহিত রহিয়াছে। এই দুর্জয় শক্তির বিস্ফোরিত হওয়া ছিল অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার।
ইসলামের মূল আকীদা- এক আল্লাহ্ ছাড়া আর কাহাকেও মানি না, ভায় করিনা, অন্য কাহারও নিকট একবিন্দু নতি স্বীকার করি না এবং রাসূলে করীম (স)ই আল্লাহ্র প্রেরিত রাসূল, আমাদের একমাত্র পথনির্দেশক- এই দৃঢ় প্রত্যয়ই ইসলামকে এ বিশ্ববিজয়ী শক্তি দান করিয়াছে। আকীদা-বিশ্বাসের এই বলিষ্ঠতাই সাধারণ মানুষকে বিপ্লবী বানাইয়া দিয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে মন ও মানসের এই স্বাধীনতা ইসলামের এক বিরাট অবদান। সেই সঙ্গে ধর্ম ও মতাদর্শের ব্যাপারে কোনরূপ বলপ্রয়োগ ছিল খিলাফতে রাশেদার সম্পূর্ণ নীতিবিরুদ্ধ। ইসলাম গ্রহণের জন্য সারা দুনিয়ার মানুষকে আহ্বান জানানো হইয়াছে বটে; কিন্তু নিজের ধর্মবিশ্বাস পরিবর্তন করার জন্য ইসলাম কাহাকেও বাধ্য করে না। তবে ইসলামের আদর্শ সম্পর্কে লোকেরা গুরুত্ব সহকারে চিন্তা-বিবেচনা করিবে, দুনিয়ার অন্যান্য ধর্ম ও মতাদর্শের সহিত উহার তুলনামূলক আলোচনা ও অধ্যয়ন করিয়া উহার বৈশিষ্ট্য নিরপেক্ষভাবে স্বীকার করিবে, ইসলামের ইহা এক বলিষ্ঠ আশাও বটে। কেননা তাহা হইলে ইহা গ্রহণ না করিয়া কেহ যে থাকিতে পারিবে না, এই সম্পর্কে ইসলাম নিঃসন্দেহ। বস্তুতঃইসলাম মানব প্রকৃতির সহিত পুরাপুরি সামঞ্জস্যশীল এক পূর্ণাঙ্গ জীবন-বিধান। সুস্থ বিবেক-বুদ্ধি পূর্ণাঙ্গ জীবনাদর্শ হিসেবে একমাত্র ইসলামকেই গ্রহণ করিতে পারে, এই বিষয়ে ইসলামের কোন সংশয় নাই।
ইসলামের মুক্তি ও স্বাধীনতার এই বিপ্লবী বাণীই দুনিয়ার অন্যান্য ধর্ম ও মতাদর্শের পক্ষে কঠিন চ্যালেঞ্জ হইয়া দেখা দিয়াছে। কেননা আকীদা-বিশ্বাস ও কর্মনীতি গ্রহণের স্বাধীনতা দেওয়া হইলে ইসলামের নির্ভুল ও পূর্ণাঙ্গ আদর্শই যে সর্ব শ্রেণীর মানুষকে প্রবলভাবে আকৃষ্ট করিবে, মানুষ নিজের ভুল ধর্ম ও মতাদর্শ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ত্যাগ করিবে, ইহা ইসলামী দাওয়াত ও আন্দোলনের এক পরীক্ষিত সত্য। আর ইহার পরে দুনিয়ার অপরাপর ধর্ম ও মতাদর্শের যে অপমৃত্যু ঘটিবে, তাহা সন্দেহাতীত। ইসলামের পূর্ণাঙ্গ আদর্শ প্রচারে দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে যে বাধার সৃষ্টি করা হয়, উহার মূলে একমাত্র এই কারণই নিহিত রহিয়াছে।
ইসলাম মনের স্বাধীনতা(Freedom of mind)-র যে বিপ্লবী আদর্শ দুনিয়ার সম্মুখে পেশ করিয়াছে, খিলাফতে রাশেদার আমলে তাহা পুরাপুরি কার্যকর ও বাস্তবায়িত হইয়াছে। এই আমলে বহুদেশ অধিকৃত হইয়াছে বহু জনপদ ইসলামের অধীনতা মানিয়া লইয়াছে; কিন্তু একজন লোককেও জোরপূর্বক স্বীয় ধর্মমত পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করা হয় নাই। কাহাকেও সে জন্য প্রলোভিত করা হয় নাই। যে লোক স্বেচ্ছায় ও সোৎসাহে ইসলাম কবুল করিয়াছে, সে অন্যান্য সব মুসলমানের মতই সমান মর্যাদা ও অধিকার লাভ করিয়াছে। পক্ষান্তরে যে লোক স্বীয় পূর্বত্ন ধর্ম ও মতাদর্শে অবিচল থাকিতে চাহিয়াছে, তাহাকেও সেইরূপ থাকিবার জন্য পূর্ণ অধিকার দেওয়া হইয়াছে। সে যাহাতে নিজস্ব ধর্ম পালনের সঙ্গে সঙ্গে স্বীয় ধন-মান ও প্রানের নিরাপত্তা সহকারে বসবাস করিতে পারে, সেজন্য ইসলামী খিলাফত পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে। বিনিময়ে তাহাদের সামর্থ্যনুযায়ী একটা বিশেষ ‘কর’(Tax) গ্রহণ করা হইয়াছে। এই কর কোন রূপ জরিমানা ছিল না। তাহাদের সার্বিক নিরাপত্তার নিশ্চিত করার জন্য রাষ্ট্রকে যে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইত, ইহা ছিল সে ব্যাপারে এক বিশেষ ধরনের চাঁদা। ইহাকে আরবী পরিভাষায় ‘জিজিয়া’বলা হয়। এই শব্দের অর্থঃ বদলা বা বিনিময়। আর বস্তুতঃ ইহা ছিল তাহার ধর্ম,ধন-মাল, মান-সম্ভ্রম ও প্রাণের নিরাপত্তা বিধানের জন্য খিলাফত কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থার বিনিময় মূল্য মাত্র। যেখানে এই নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণের দায়িত্ব পালনে খিলাফত অক্ষম হইয়াচে,সেখানে ইহা গ্রহণ শুধু বন্ধই করা হয় নাই,পূর্ব গৃহীত করও ফেরত দেওয়া হইয়াছে। ইসলামী ইতিহাসের পৃষ্ঠায় একথা সুস্পষ্টভাবে ও স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে।
বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর প্রতি বিশ্বাসী ও তাঁহার জন্য উৎসর্গীকৃত প্রাণ লোকদের হাতে প্রতিষ্ঠিত এই রাষ্ট্র ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপিত ছিল ব্যক্তি স্বাধীনতা, মৌলিক মানবীয় অধিকার, নির্বিশেষে সাম্য ও ভ্রাতৃসুলভ প্রেম-প্রীতি ও ভালোবাসার উন্নত নীতিমালা ও আদর্শের উপর। ইহা ছিল রোমান রাজতন্ত্রবাদের সম্পূর্ণ বিপরীত ধরনের এক রাষ্ট্র ব্যবস্থা। অন্যদিকে সাধারণ মানবীয় কল্যাণের দৃষ্টিতে আধুনিকতম তথাকথিত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থাও উহার তুলনায় অত্যন্ত দীন-হীন। বস্তুত অনারব লোকদিগকে আরবের অধীন-অনুগত বানানো খিলাফতে রাশেদার কোন লক্ষ্য ছিল না। তদানীন্তন রোমান ও পারসিকদের নিকৃষ্টতম দাসত্ব হইতে মুক্ত করিয়া আরবদের দাসত্ব নিগড়ে উহাদিগকে বন্দী করাও ছিল না উহার উদ্দেশ্য; বরং মানুষকে সর্বপ্রকার মানবিক ও বৈষয়িক গোলামী হইতে পরিপূর্ণ মুক্তিদান, একমাত্র সৃষ্টিকর্তার বন্দেগী ও রাসূলের নেতৃত্ব স্বীকার করিয়া দ্বীন-ইসলামের মহান বিধান অনুযায়ী সম্পূর্ণ স্বাধীন পরিবেশে জীবন যাপন ও বিকাশ-বর্ধনের অবাধ-উদার ও উন্মুক্ত সুযোগ করিয়া দেওয়াই ছিল উহার যাবতীয় চেষ্টা-প্রচেষ্টা ও সাধনা-সংগ্রামের চরমতম লক্ষ্য। ইসলামের সুমহান আদর্শে ঐকান্তিক বিশ্বাস এবং পরস্পরের গভীর ভ্রাতৃত্ব ও একনিষ্ঠ প্রেম-প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হওয়াই ছিল উহার একমাত্র উপায়। খিলাফতে রাশেদার আমলে বিজয়ী ও বিজিত বলিতে কোন শ্রেণী-বিভেদ ছিল না। সর্বশ্রেণী- সকল স্তর ও পর্যায়ের মানুষের সেখানে পুরাপুরি সমান অধিকার ও মর্যাদালাভে ধন্য হইয়াছিল। ভাষা,গোত্র ও অঞ্চলের ভিত্তিতে তাহাদের মধ্যে কোন পার্থক্য ও তারতম্য ছিল না। এমন কি ইরাক ও সিরিয়ার অমুসলিম এবং নাজরান ও আরবের অন্যান্য এলাকার খৃষ্টানদের মধ্যেও কোনরূপ পার্থক্য সৃষ্টি হইতে দেওয়া হয় নাই। মুসলমানগণ তাহাদের মধ্যে ইসলাম প্রচারের কাজ করিতেন বটে; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও যাহারা নিজেদের পৈতৃক ধর্মে অবিচল থাকিতে চাহিত, তাহাদিগকে সেইরূপ থাকারই পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছিল। খিলাফতে রাশেদার আমলে ধর্ম গ্রহণের ব্যাপারে কুরআনের নিম্নোদ্ধৃত ঘোষণাদ্বয় পুরামাত্রায় কার্যকর ছিলঃ
******(আরবী)
দ্বীন ও ধর্মের ব্যাপারে কোনরূপ বল প্রয়োগ বা জোরজবরদস্তির স্থান নেই।
যে লোক হেদায়েত গ্রহণ করে, উহার কল্যাণে সে নিজেই লাভ করিবে। আর যে লোক পথভ্রষ্ট হইয়া থাকিতে চাহে, উহার ক্ষতি ও অকল্যাণ তাহাকেই ভোগ করিতে হইবে। হে রাসূল আপনি লোকদিগকে বলিয়া দিন,তোমাদের পর্যন্ত সত্যের বাণী পৌঁছাইয়া দেওয়াই আমার কাজ; গ্রহণ করা বা না করা তোমাদের নিজেদের দায়িত্ব। তোমাদের হেদায়েত বা গুমরাহীর কোন দায়িত্ব আমার উপর বর্তায় না।
খিলাফতে রাশেদার আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা
খিলাফতে রাশেদার রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় ইসলামী সমাজ-সভ্যতা ও কৃষ্টি-তামাদ্দুনের পূর্ণ বাস্তবায়ন নিস্পন্ন হইয়াছিল।ইহা একাধারে ছিল দ্বীন-ভিত্তিক ও বৈষয়িক উন্নয়নের একমাত্র নিয়ামক রাষ্ট্র। দ্বীন-ইসলামের উপরই উহার ভিত্তি স্থাপিত ছিল এবং কুরআনের অকাট্য মূলনীতি ও রাসূলে করীম(স)- এর সুন্নাত অনুযায়ী মানবতার সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ সাধনই ছিল উহার যাবতীয় চেষ্টা-সাধনার একমাত্র লক্ষ্য।
খিলাফতে রাশেদার আমলে কুরআন মজীদ ও সুন্নাতে রাসূল মুতাবিকই যাবতীয় আইন-কানুন প্রণয়ন করা হইত। খুলাফায়ে রাশেদুন যদি এমন কোন সমস্যা বা জিজ্ঞাসার সম্মুখীন হইতেন,যাহার প্রত্যক্ষ মীমাংসা কুরআন ও হাদীস হইতে লাভ করিতে পারিতেন না, তাহা হইলে নবী করীম(স)-এর কার্যাবলীর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সম্মুখে রাখিয়া উত্তমভাবে উহার মিমাংসা করিয়া লইতেন এবং কোন দিক দিয়াই কুরআন ও সুন্নাতে রাসূলের মৌলিক আদর্শ লংঘিত হইতে দিতেন না।
ইসলামের মৌলিক বিধান অনুসারে গোটা উম্মতে মুসলিমা খলীফাদের আনুগত্য স্বীকার করিয়া চলিতে বাধ্য ছিল। কিন্তু সেই সঙ্গে এই মূলনীতিও সর্বাপেক্ষা সমর্থিত ছিল যে, আল্লাহ্ ও রাসূলের হুকুম-বিধানের বিরুদ্ধতা করিয়া কোন খলীফা বা রাষ্ট্রকর্তার আনুগত্য করা যাইতে পারে না। কুরআন-হাদীসের মূল সূত্র হইতে বাস্তব ও ব্যবহারিক জীবনের খুঁটিনাটি আইন-কানুন প্রনয়নের অধিকারের ক্ষেত্রে খলীফার কোন প্রাধান্য, বিশিষ্টতা ও অগ্রাধিকার স্বীকৃত ছিল না। অনেক ক্ষেত্রে খলীফা বরং অন্যান্য সাহাবীদের নিকট কুরআন-হাদীস-ভিত্তিক রায় বা পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতেন। এই ব্যাপারে খলীফাদের সঙ্গে দ্বিমত হওয়ারও পূর্ণ অধিকার ছিল। শুধু তাহাই নয়,খলীফাদের রায়ের ভুল-ভ্রান্তি ধরাইয়া দেওয়া এবং তাঁহাদের প্রকাশ্য সমালোচনা করার সাধারণ অধিকারও সর্বতভাবে স্বীকৃত ছিল।
জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত রায় বা সম্মতি অনুযায়ী খলীফা নির্বাচিত হইতেন। জোরপূর্বক কিংবা বংশানুক্রমিক ধারা অনুযায়ী খলীফার পদ দখল করা শুধু ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থারই খেলাফ নহে, ইসলামী বিধানের দৃষ্টিতে উহা মারাত্মক অপরাধও বটে। খুলাফায়ে রাশেদুনের মধ্যে বাদশাহী শান-শওকাত কিংবা ডিকটেটরী স্বৈরতন্ত্রের কোন অস্তিত্তই বর্তমান ছিল না। তাঁহারা নিজদিগকে নাগরিকদের সমপর্যায়ভুক্ত মনে করিতেন। একমাত্র খিলাফত ভিন্ন অন্য কোন দিক দিয়াই তাঁহাদের ও সাধারণ জনগণের মধ্যে একবিন্দু পার্থক্য ছিল না। খলীফার দরবারে সরকারী কর্মচারী ও জনসাধারণের অবাধ যাতায়াত ছিল এবং এই ব্যাপারে কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতার অবকাশ ছিল না। এই কারণে জনগণের সাধারণ অবস্থা ও অভাব-অভিযোগ সম্পর্কে প্রত্যক্ষভাবে ওয়াকিফহাল হওয়া এবং কোন প্রকার দীর্ঘসূত্রিতা ব্যতিরেকেই উহার প্রতিকার করা তাঁহাদের পক্ষে অত্যন্ত সহজ ছিল।এই কারণেই এ কথা উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করা যাইতে পারে যে, খিলাফতে রাশেদাই হইতেছে বিশ্ব- ইতিহাসে একমাত্র ও সর্বপ্রথম রাষ্ট্র, যেখানে প্রকৃত গণ-অধিকার পুরাপুরিভাবেই রক্ষিত হইয়াছে।
বিচার বিভাগ
খুলাফায়ে রাশেদুনের আমলে বিবদমান দুইপক্ষের মধ্যে ইনসাফ বা ন্যায় বিচার নিশ্চিত করা খলীফার অন্যতম দায়িত্ব মনে করা হইত। এইজন্য প্রথম দিকে তাঁহারা প্রায় সব বিচারকার্য নিজেরাই সম্পন্ন করিতেন। অবশ্য দূরবর্তী স্থানসমূহের জন্য নিজেদের তরফ হইতে প্রতিনিধি নিযুক্ত করিতেন। প্রথম খলীফার আমলে প্রত্যেক শহরের জন্য নিযুক্ত শাসনকর্তাই বিচার কার্য আঞ্জাম দিতেন। কিন্তু দ্বিতীয় খলীফা তাঁহার খিলাফত আমলে বিচার বিভাগকে সম্পূর্ণ স্বাধীন ও স্বতন্ত্র করিয়া দিয়াছিলেন। এইজন্য প্রত্যেক শহরেই স্বতন্ত্র মর্যাদাসম্পন্ন বিচারপতি বা কাজী নিয়োগ করা হইয়াছিল। বিচার বিভাগ প্রসাশন বিভাগের কর্তৃত্ব হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও স্বাধীন মর্যাদাসম্পন্ন ছিল। বিচারপতি রায়দানের ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিলেন। খলীফার পক্ষ হইতে তাঁহাদিগকে এই নির্দেশ দান করা হইত যে, তাঁহারা বিচারে যে রায়ই দান করিবেন, তাহা যেন সর্বতোভাবে কুরআন ও সুন্নাতে-রাসূলের ভিত্তিতে সম্পন্ন হয়। কোন দিক দিয়াই যেন উহা লংঘন করা না হয়। সংশ্লিষ্ট এলাকার শাসনকর্তা বিচারপতির উপর কোন প্রকার প্রভাব বিস্তার কিংবা প্রভুত্ব খাটাইতে পারিতেন না। কাজী বা বিচারপতি সরাসরি খলীফা কর্তৃত্ব নিযুক্ত হইতেন। সংশ্লিষ্ট শহরের শাসনকর্তাকেও অনেক সময় বিচারপতি নিয়োগের ইখতিয়ার দান করা হইত; কিন্তু তাহা ছাড়া বিচারপতি নিয়োগের ব্যাপারে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা হইত। চতুর্থ খলীফার প্রদত্ত একখানি নিয়োগপত্রের নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতে ইহার বাস্তব প্রমাণ পাওয়া যায়। লোকদের মামলা –মুকাদ্দমা নিস্পত্তি করার জন্য এমন সম্মানিত ব্যক্তিদের নিয়োগ কর,যাহাদের রায় জনগণ অকুণ্ঠিত চিত্তে মানিয়া লইবে এবং কেহ উহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার কোন সাহস বা প্রয়োজন বোধ করিবে না। তাঁহারা হইবেন সকল প্রকার লোভ-লালসা ও মোহ-মাৎসর্য হইতে পবিত্র। তাঁহারা কাহারো বিশেষ মর্যাদার কারণে সন্ত্রস্ত ও প্রভাবান্বিত হইবেন না। সকল ব্যাপারেই তাঁহাদিগকে গভীর-সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বশীল হইতে হইবে। সন্দেহ-সংশয়পূর্ণ ব্যাপারে তাঁহারা অত্যন্ত সতর্ক হইবেন। পক্ষদ্বয়ের উপস্থাপিত যুক্তিপূর্ণ প্রমাণ ও সাক্ষ্য সন্দর্শনে কিছুমাত্র ঘাবড়াইয়া যাইবেন না, প্রতিটি ব্যাপারের গভীর তলদেশে পৌঁছিবার জন্য পরিপূর্ণ সতর্কতা ও চিন্তা-গবেষণা সহকারে কাজ করিবেন। এইভাবে তাঁহারা কোন চূরান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়া গেলে তাহা পুরাপুরি দৃঢ়তা সহকারে কার্যকর করিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হইবেন না। কোন প্রকার সুপারিশ ও কোনরূপ পদ-মর্যাদাকেই তাঁহারা ফয়সালা কার্যকর করার পথে বাধা হইয়া দাঁড়াইতে দিবেন না। যদিও এই ধরনের লোকদের সংখ্যা বেশী হয় না কখনো, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও বিচারপতিকে অবশ্যই উল্লেখিত গুণে ভূষিত হইতে হইবে। তোমরা যখন কাহাকেও বিচারপতি নিযুক্ত করিবে, তখন তাহার যথেষ্ট পরিমানে বেতন ধার্য করিবে; তাহা হইলে তাহার জীবনযাত্রা নির্বাহের দাবি তাহাকে ঘুষ লইতে বাধ্য করিবে না। উপরন্তু তোমাদের মন-মানস ও সমাজ-সম্মেলনে তাহার মর্যাদা উন্নত হওয়া বাঞ্ছনীয়, যেন তাহার বিরুদ্ধে প্রচারণা চালাইবার সাহস কাহারো না হয়।
বিচারকগণ ছাড়াও প্রত্যেক শহরেই ইসলামী আইন সম্পর্কে বিশেষ দক্ষতাসম্পন্ন একটি জনগোষ্টী সব সময়ই মওজুদ থাকিত। কোন ব্যাপারে বিচারকদের অসুবিধা বা সমস্যা দেখা দিলে ইহাদের নিকট হইতে সাহায্য গ্রহণ করা হইত।
এই সময় নবী করীম(স)-এর হাদীসসমূহ গ্রন্থাবদ্ধ ছিল না, তাহা ছিল লোকদের স্মৃতিপটে রক্ষিত। কেহ একটি হাদীস জানিত আর কাহারো স্মরণ ছিল অন্য একটি হাদীস। সমস্ত হাদীস এককভাবে বিশেষ কাহারো স্মরণ ছিল না আর ইহাই ছিল সেকালের একটি কঠিন সমস্যা। বিচারকদের সম্মুখে উপস্থিত ব্যাপারের মীমাংসা করার জন্য কোন হাদীসের প্রয়োজন হিলে তাঁহারা বিভিন্ন লোকের নিকট জিজ্ঞাসা করিতেন এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে রাসূলে করীম(স)-এর নির্দেশ বা কর্মনীতি জানিতে চেষ্টা করিতেন। ফলে তাঁহারা রাসূলের যে হাদীসি পাইতেন, সেই অনুযায়ী বিচার-ফয়সালা করিতেন; কিন্তু সুনির্দিষ্ট কোন হাদীস পাওয়া না গেলে ইসলামের সামগ্রিক ব্যবস্থা ও উহার ধারাকে সম্মুখে রাখিয়া তাঁহারা ইজতিহাদ করিতেন। এই কারণে অনেক সময় কোন নির্দিষ্ট ব্যাপারে বিচারকের বিভিন্ন প্রকার হইত। বিচারকদের ফয়সালাসমূহ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখার তখনো শুরু হয় নাই। ফলে পরবর্তীকালের লোকেরা উহা হইতে কিছুমাত্র ফায়দা লাভ করিবার সুযোগ পাইত না।
এই যুগের যাবতীয় বিচার কার্য কেবলমাত্র ইজতিহাদের উপর নির্ভরশীল ছিল বলিয়া কাহারো কাহারো মনে প্রশ্ন জাগিতে পারে; কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার তাহা নহে। কেবলমাত্র শরীয়াতের খুঁটিনাটি আইন জানিবার ও যুগের বিশেষ অবস্থা ও ঘটনার উপর উহাকে প্রয়োগ করার ব্যাপারেই ইজতিহাদ-নীতি ব্যবহার করা হইত। স্মর্তব্য যে,ইসলামী আইনসমূহ ছিল কতকগুলি মূলনীতির সমষ্টি; উহার খুঁটিনাটি বিধান তখনো রচিত হয় নাই। বস্তুত চিরকাল ও সমগ্র মানবতার জন্য প্রদত্ত আইন-বিধান এইরূপ হওয়াই স্বাভাবিক। কালের প্রতিটি পর্যায়ে ও পৃথিবীর প্রতিটি অঞ্চলেই উহার বাস্তব প্রয়োগ কেবলমাত্র এই ভাবেই সম্ভব ও সহজ হইতে পারে।
বিচারক নিয়োগের পরও জনগণের ঝগড়া-বিবাদ মীমাংসা করার ব্যাপারে খলীফাদের প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহনে কোন বাধা ছিল না; বরং অনেক ক্ষেত্রে তাঁহারা নিজেরাই অনেক ঝগড়া-বিবাদ মীমাংসা করিতেন। সেইসব ক্ষেত্রে নিযুক্ত বিচারকগন শুধু খলীফাদের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করিতেন মাত্র।
দেশরক্ষা বিভাগ
খিলাফত আমলে যুদ্ধ বা সৈন্যবাহিনী পরিচালনা করার মূল ক্ষমতা খলীফার হস্তেই নিবদ্ধ থাকিত। কেননা নবী করীম (স)-এর জামানায়ও এই রীতিই কার্যকর ছিল। তিনি নিজেই সৈন্যবাহিনীর নেতৃত্ব দিতেন। কিন্তু পরবর্তীকালে শাসন পরিধি যখন বিশালতর হইতে লাগিল, তখন খলীফাগণ সর্বশ্রেষ্ঠ বীর ও যোদ্ধা হওয়া সত্ত্বেও পৃথকভাবে সেনাধ্যক্ষের নিযুক্তি শুরু হইল। তাহাকে মানিয়া চলা স্বয়ং খলীফাকে মানিয়া চলার মতই অবশ্যই কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। যুদ্ধের অবসান হইলে সামরিক ব্যাপারসমূহ পর্যবেক্ষণ ও ভবিষ্যতের জন্য তাহাদিগকে ট্রেনিং দান করিই হইত সেনাধ্যক্ষদের একমাত্র কাজ।
হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)- এর খিলাফত আমলে সমগ্র সৈন্যবাহিনী অবৈতনিক ও স্বেচ্ছামূলক ছিল। কোন রেজিস্ট্রি বহিতে তাহাদের নাম লিপিবদ্ধ ছিল না। হযরত উমর ফারুক (রা)-এর খিলাফত কালেই সৈন্য বিভাগ সুষ্ঠু ও সুসংবদ্ধভাবে গঠিত হয় ও প্রতিটি সৈনিকের নাম রেজিস্ট্রিভুক্ত হয়। ইহার ফলে সৈন্যবাহিনীতে শৃঙ্খলা স্থাপিত হয়। কোন সৈনিক পলায়ন করিলে কিংবা পশ্চাতে থাকিয়া গেলে অতি সহজেই তাহা ধরা পড়িত। পলাতক সৈনিকদের জন্য তখন একটি বিশেষ ধরনের শাস্তি নির্দিষ্ট ছিল। পলাতকের নিজ মহল্লার মসজিদে তাহার নাম প্রকাশ ও প্রচার করিয়া ঘোষণা করা হইত যে,এই ব্যক্তি জিহাদের ময়দান হইতে পলাইয়া আসিয়াছে;আল্লাহ্র পথে আত্মদান করার ব্যাপারে সে কুণ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছে। বস্তুতঃ এতটুকু ভৎসনা আরবের জন্য মৃত্যুদণ্ড অপেক্ষাও সাংঘাতিক ছিল। কেননা সমগ্র বিশ্ব-জাতির মাঝে আরবদের যে অতুলনীয় বীরত্ব ও বিস্ময়কর সাহসিকতার অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপিত হইয়াছিল, তাহাতে কোন ব্যাক্তিকে অপৌরুষ ও ভীরুতার দায়ে অভিযুক্ত কয়া এবং প্রকাশ্যভাবে উক্তরুপে ঘোষণা দেওয়া মৃত্যু অপেক্ষাও অনেক কঠিন ব্যাপার ছিল। অতঃপর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে সমাজে মুখ দেখাইবার কোন স্থান আর অবশিষ্ট থাকিত না।
হযরত উমর(রা) সমস্ত সৈনিকদের জন্য বায়তুলমাল হইতে বেতন নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। এই বেতনের কোন নির্দিষ্ট হার ছিলনা। ইসলামী আদর্শ অনুসরণের ক্ষেত্রে শ্রেষ্টত্ত ও প্রাধান্যই ছিল মুজাহিদদের বেতন নির্ধারণের একমাত্র মাপকাঠি। অবশ্য শেষ পর্যায়ে হযরত আলী (রা) এই পার্থক্যও খতম করিয়া দিয়া সকলের জন্য সমান মানের বেতন চালু করিয়াছিলেন।
ইসলামী বাহিনীতে প্রত্যেক দশজন সৈনিকের উপর একজন ‘প্রধান’ নিযুক্ত হইত।আরবী সামরিক পরিভাষায় তাহাকে বলা হইত ‘আরীফ’। এই আরীফদের হস্তেই সকল সৈনিকদের বেতন অর্পণ করা হইত; তাহারা অধীনস্থ সৈনিকদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিত।
সৈন্যবাহিনী সংগঠনের ব্যাপারে খুলাফায়ে রাশেদুনের আমলে যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়। প্রাক-ইসলাম যুগে আরবগণ শত্রুপক্ষকে কখনো সারিবদ্ধভাবে আর কখনো বিচ্ছিন্নভাবে মুকাবিলা করার জন্য অগ্রসর হইত। প্রথমে উভয় পক্ষ হইতে এক-দুইজন বীরপুরুষ সম্মুখ-সমরে লিপ্ত হইত,তাহার পর সাধারণ হামলা পরিচালিত হইত এবং শেষ পর্যন্ত এলোমেলোভাবে আক্রমণ ও অস্ত্র পরিচালনা করা হইত। মুসলমানগণও ইসলামী জিহাদের প্রথম পর্যায়ে এই রীতিরই অনুসরণ করিতেছিলেন। কিন্তু উত্তরকালে তাহারা যখন পারস্য ও রোমানদের সুসংগঠিত সৈন্য বাহিনীর মুখামুখী হইতে আরম্ভ করিলেন, তখন তাঁহারা সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিলেন যে, আধুনিক পদ্ধতিতে এই সংগঠিত সৈন্যবাহিনী ও সমর নীতির মুকাবিলা করিতে হইলে প্রাচীন রীতি অবশ্যই পরিহার করিতে হইবে। অতঃপর তাহারা নূতনভাবে নিজেদের সৈন্যবাহিনী গড়িয়া তোলেন ও সম্পূর্ণ আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করিতে শুরু করেন। যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যবাহিনীকে সুষ্ঠুরূপে সারিবদ্ধ করা হইতে লাগিল, কেহ অগ্রে বা পশ্চাতে পড়িয়া থাকিত না। গোটা সৈন্যবাহিনীকে মোটামুটি পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করা হইত। সকলের অগ্রবর্তী বাহিনীকে বলা হইত ‘মুকদ্দমা’, যুদ্ধের সূচনা করাই হইত ইহার দায়িত্ব। মধ্যবর্তী বাহিনীকে বলা হইত ‘কলব’, মূল সেনাধ্যক্ষ ইহাদের দ্বারাই পরিবেষ্টিত থাকিতেন। ডান পার্শ্বে স্থাপিত বাহিনীকে বলা হইত ‘মায়মানা’ এবং বাম পার্শ্বে অবস্থিত ‘মায়সারা’। আর সকলের পশ্চাতে অবস্থিত বাহিনীর নাম দেওয়া হইত ‘সাকাহ’।
যে সৈন্যবাহিনী এই পাঁচটি উপ-বাহিনীতে বিভক্ত হইত, উহাকে ‘খামীস’ বলা হইত। ইহার প্রত্যেক অংশেরই একজন করিয়া ‘আমীর’ হইতেন এবং তিনি মূল সেনাধ্যক্ষের ফরমান অনুসারে নিজ নিজ বাহিনী পরিচালনা করিতেন।অশ্বারোহী বাহিনীর আমীর হইতেন স্বতন্ত্র। পশ্চাদ্দিক সংরক্ষণের জন্য মুসলিম সৈনিকগন বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করিতেন,যেন শত্রু-সৈন্য কোন সুযোগেই পশ্চাদ্দিক হইতে তাহাদের উপর হামলা করিতে সমর্থ না হয়। নৈশকালীন আক্রমণ হইতে গোটা বাহিনীকে হেফাজত করার জন্য তাঁহারা বিশেষ ব্যবস্থা ও কর্মপন্থা গ্রহণ করিতেন। মুসলমানদের সামরিক গোয়েন্দা বিভাগ ছিল সর্বাধিক সুসংগঠিত ও সুসংবদ্ধভাবে সক্রিয়। সেই কারণে শত্রুদের অধিকাংশ গোপন ইচ্ছা বা পরিকল্পনা তাঁহারা পূর্বাহ্ণেই জানিতে পারিতেন।
রাজস্ব বিভাগ
হযরত উমর (রা)-এর খিলাফত কাল হইতে রাজস্ব আদায়ের জন্য স্বতন্ত্র ও স্থানীয়ভাবে লোক নিয়োগ করা হইত। প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের উপর রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব সাধারণতঃ অর্পণ করা হইত না। আদায়কৃত রাজস্ব খলীফার নির্দেশ অনুসারে সৈনিকদের বেতন-ভাতা ও জনকল্যাণমূলক অন্যান্য সর্বজনীন কাজকর্মে ব্যয় করা হইত। উদ্ধৃত অর্থ কেন্দ্রীয় রাজধানীতে পাঠাইয়া দেওয়া হইত।
খিলাফত আমলে দুই প্রকারের রাজস্ব ধার্য করা হইতঃ(১)স্থায়ী ও (২)অস্থায়ী। স্থায়ী রাজস্বের মধ্যে যাকাত,উশর ও জিজিয়া উল্লেখযোগ্য। পক্ষান্তরে গনিমতের মাল ছিল অস্থায়ী রাজস্ব বা রাষ্ট্রীয় আয়।
খারাজ
সাধারনতঃযুদ্ধ-জয়ের ফলে অধিকৃত দেশের যাবতীয় চাষযোগ্য জমি উহার পূর্বতন মালিকদের নিকটই থাকিতে দেওয়া হইত। অবশ্য উৎপন্ন ফসলের একটি নির্দিষ্ট অংশ রাজস্ব বাবদ আদায় করিয়া লওয়া হইত। ইহাকেই ইসলামী পরিভাষায় বলা হয় ‘খারাজ’। ইহাকে ভোগ্য জমির খাজনা মনে করা যাইতে পারে। কোন কোন ক্ষেত্রে আবার জমির পরিমাণ অনুযায়ী নির্দিষ্ট মুদ্রা কর-বাবদ ধার্য করা হইত।
উশর
যেসব জমির মালিকগণ ইসলাম কবুল করিত অথবা বিজয়ী মুসলমানরা যেসব জমির মালিকদের নিকট হতে জিজিয়া আদায় করিতেন না, সেই জমিকে বলা হয় উশরী জমি এবং উহার ফসলের এক দশমাংশ কিংবা বিশ ভাগের এক ভাগ সরকারী ব্যবস্থাপনায় আদায় কর হইত। মুসলমানগণ বল প্রয়োগ বা যুদ্ধের পরিণতিতে যেসব জমি দখল করিতেন, তাহা ‘উশরী’ জমি নামে অভিহিত হইত এবং তাহা কেবলমাত্র মুসলমানদের মধ্য বণ্টন করিয়া দেওয়া হইত। ফলে তাহা মুসলমানদেরই দখলিভুক্ত হইয়া থাকিত।
হযরত উমর (রা)- এর খিলাফতকালে যখন সিরিয়া ও ইরাক অধিকৃত হয়, তখন তিনি বিজিত জমি সম্পর্কে উপদেষ্টাদের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে,উহার বিলি-ব্যবস্থা কি ভাবে কর হইবে? অধিকাংশ লোকই জমিগুলিকে মুসলমানদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়ার পরামর্শ দিয়াছিলেন।
হযরত উমর (রা)বলিয়াছিলেনঃ ‘তাহা হইলে তো ভবিষত বংশধরদের হক নষ্ট করা হইবে। কেননা, বর্তমানে জমিসমূহ বণ্টন করিয়া দিলে অনাগত মানুষদের জন্য কিছুই অবশিষ্ট থাকিবে না’। উহাতে হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ(রা)বলিলেনঃ জমি ও দাস-দাসী তাহারাই পাইবার অধিকারী, যাহারা নিজেদের বাহুবলে দেশ জয় করিয়াছে; অন্য লোকদের তাহাতে কি অধিকার থাকিতে পারে? ইহার উত্তরে খলীফা উমর ফারুক (রা) বলিলেনঃ ‘একথা ঠিক, কিন্তু মনে রাখিও আমার পর খুববেশী দেশ জয়ের সম্ভবনা থাকিবে না বলিয়া তখন মুসলমানদের পক্ষে অধিক পরিমাণ মাল-দৌলত ও জমি লাভ করা সম্ভব হইবে না। উত্তরকালে বরং অনেক দেশজয় কল্যাণের পরিবর্তে দুর্বহ বোঝার কাজই করিবে বেশী। ইরাক ও সিরিয়ার জমি উহার মালিকদের নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়া ও বিজিত লোকদেরকে ক্রীতদাস বানাইয়া বিজয়ী মুসলামানের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিলে সীমান্তের সংরক্ষণ ব্যবস্থা কিরূপে কার্যকর হইবে? কেননা মুসলামানগণ তো কৃষিকাজে ব্যস্ত হইয়া পড়িবে। এতদ্ব্যতীত ইয়াতীম ও অসহায় বিধবাদের ভরণ-পোষণের কাজও অসমাপ্তিই থাকিয়া যাইবে’।
খলীফা উমর ফারুক(রা)-এর এই ভাষণ শ্রবণ করার পর সকলে একবাক্যে বলিয়া উঠিলেনঃ “আপনার মত বাস্তবিকই সঠিক ও নির্ভুল, তাহাতে সন্দেহ নাই। সীমান্তে ও শহরে যদি সৈন্যবাহিনী নিয়োজিত না থাকে, তাহা হইলে এইসব এলাকা সংরক্ষণ করার কোনই ব্যবস্থা থাকিবে না এবং ইসলামের দুশমনগণ পুনরায় এই শহরগুলির উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া বসিবে”।হযরত উমর বলিলেনঃ এই ব্যাপারটি তো পরিস্কার হইয়া গেল। এখন আমার এমন একটি লোকের প্রয়োজন, যিনি খারাজ নির্ধারণের জন্য সমগ্র ইরাকের জরীপ কার্য সম্পাদনের দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন’। অতঃপর উমরান ইবন হানীফকে এই কাজে নিযুক্ত করা হইল। তিনি অত্যন্ত পরিশ্রম সহকারে এই কাজ সম্পন্ন করিলেন এবং হযরত উমর (রা)- এর শাহাদাত লাভের এক বৎসর পূর্বেই সওয়াদে কুফা হইতে আদায়কৃত খারাজের পরিমাণ এক কোটি মুদ্রা পর্যন্ত পৌঁছিয়াছিল।
সিরিয়া বিজয়ের পরও সৈনিকদের পক্ষ হইতে অধিকৃত জমি সৈনিকদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়ার দাবি উত্থাপিত হয়। কিন্তু তখনও হযরত ফারুকে আজম (রা) উক্তরুপ জওয়াব দিয়া সকলকে নিরস্ত করেন। ফলে ইরাকের ন্যায় সিরিয়ার ভূমি হইতেও বিপুল পরিমাণ খারাজ সরকারী খাজাঞ্জীতে সঞ্চিত হইতে থাকে।
বস্তুতঃ বিজিত এলাকার জমিক্ষেত বিজয়ীদের মধ্যে বণ্টন না করিয়া পুরাতন বাসিন্দাদের দখলে উহা থাকিতে দেওয়া এবং তাহাদিগকে উহার চাষাবাদ করার সুযোগ দিয়া তাহাদের নিকট হইতে খারাজ আদায় করা সম্পর্কে হযরত উমর ফারুক (রা)- এর অভিমত অত্যন্ত দূরদর্শীতার পরিচায়ক ছিল। তখন এইরূপ ফয়সালা গৃহীত না হইলে মুসলিম জাতি তাহার আসল দায়িত্ব ভুলিয়া গিয়া ক্ষেত-খামার লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িত এবং সামরিক দক্ষতা হারাইয়া ফেলিত।দ্বিতীয়তঃসেই এলাকার সংরক্ষণকারী ও অন্যান্য দেশ ও অঞ্চলে যুদ্ধলিপ্ত ইসলামী সৈনিকদের প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহেরও কোন ব্যবস্থা করা সম্ভব হইত না। আর ইহাই হইত সর্বাপেক্ষা মারাত্মক ও অপূরনীয় ক্ষতি। কেননা, এই সুযোগে পারসিক ও রোমক সরদার যা নিজেদের দেশের উপর মুসলিম আধিপত্য স্থাপিত হওয়ায় দেশত্যাগ করিয়া অন্যত্র আশ্রয় লইয়াছিল তাহারা পুনরায় নিজেদের দেশ দখল করিয়া বসিতে পারিত ও মুসলমানদের উপর প্রবলভাবে আক্রমণ চালাইত।
জিযিয়া
ইসলামী খিলাফতে যিম্মিদের(অমুসলিম অনুগত নাগরিকদের) নিকট হইতে তাহাদের জান-মাল ও ইজ্জত-আবরু সংরক্ষণ ও উহার নিরাপত্তার বিনিময়ে যে অর্থ গ্রহণ করা হইত, ইসলামী পরিভাষায় উহাকে ‘জিযিয়া’ বলা হয়। ইহা কেবলমাত্র বয়স্ক ও সুস্থ-সবল পুরুষদের নিকট হইতেই আদায় করা হইত। নারী,শিশু, দরিদ্র ও পঙ্গুদের উপর ইহা ধার্য করা হইত না। হযরত উমর (রা) বহু দরিদ্র যিম্মীর জন্য বায়তুলমাল হইতে বৃত্তি মঞ্জুর করিয়াছিল। ‘জিযিয়া’ ধার্য হইত ব্যক্তির আর্থিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এবং উহার পরিমাণ ১২ দিরহামের কম ও ২৮ দিরহাম অপেক্ষা বেশী হইত না। হযরত উমর (রা) তাহার পরবর্তী খলিফাদিগকে যিম্মীদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন, নম্র আচরণ করা, প্রতিশ্রুতি পালন ও তাহাদের জান-মাল সংরক্ষণের জন্য লড়াই করা এবং তাহাদের উপর সামর্থ্যাপেক্ষা অধিক দায়িত্ব-ভার অর্পণ না করার জন্য বিশেষভাবে উপদেশ দান করিয়াছেন।
যাকাত
খিলাফতের আমলে মুসলমানদের সকল প্রকার সঞ্চিত ধন,গৃহপালিত পশু, নগদ সম্পদ ও জমির ফসলের উপর কুরআন ও সুন্নাহ মুতাবিক যাকাত ধার্য করা হইয়াছিল। এই যাকাত রীতিমত আদায় করা হইত এবং উহার প্রাপক আটটি শ্রেণীর মধ্যে উহা বণ্টন করা হইত।
শুল্ক
মুসলিম ব্যবসায়ীগণ যখন বিদেশে নিজেদের পণ্য রফতানি করিতেন, তখন তাঁহাদের নিকট হইতে সেই দেশ এক দশমাংশ শুল্ক বাবদ আদায় করা হইত।হযরত উমর (রা) যখন ইহা জানিতে পারিলেন, তখন তিনিও ইসলামী রাজ্যে আমদানিকৃত পণ্যের উপর অনুরূপ পরিমাণ শুল্ক ধার্য করার নির্দেশ দান করিলেন। এতদ্ব্যতীত যিম্মী ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে বিশভাগের একভাগ ও মুসলিম ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে সমগ্র সম্পদের চল্লিশভাগের একভাগ আদায় করা হইত। তবে দুইশত দিরহামের কম মূল্যের সম্পদের উপর কিছুই ধার্য করা হইত না।
মুদ্রা
আরবদেশের ইসলামের পূর্বে স্বর্ণ ও রৌপ্যের ইরানী ও রোমীয় মুদ্রা প্রচলিত ছিল। নবী করীম(স) ও হযরত আবূ বকরল (রা)-এর খিলাফত কালেও এই মুদ্রাই চালু ছিল। ইরান বিজয়ের পর হযরত উমর(রা) দিরহামের ওজন করিবার ইচ্ছা ব্যক্ত করিয়াছিলেন। কেননা ইরানী মুদ্রায় ওজন বিভিন্ন প্রকারের হইত। মোট কথা খিলাফতে রাশেদার আমলে আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার পূর্ণাঙ্গ রূপ বর্তমান ও কার্যকর ছিল এবং উহা কোন দিক দিয়াই পশ্চাদবর্তী ছিল না।
হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)
ইসলামী গণ-রাষ্ট্রের প্রথম খলীফা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক(রা)। ইসলামের ইতিহাসে রাসূলে করীম হযরত মুহাম্মাদ(স)-এর পরেই হযরত আবূ বকর (রা)-এর স্থান। ইসলামী ঐতিহ্যের দিক দিয়াও রাসূলের পর তিনিই সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য ব্যাক্তি। নবী করীম(স) তাঁহার তেইশ বৎসরকালীন সাধনার মাধ্যমে যেখানে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ জীবনাদর্শ উপস্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে আরবের কঠিন জাহিলিয়াতের প্রাসাদ চুরমার করিয়া উহার ধ্বংসস্তূপের উপর ইসলামের উজ্জ্বল আদর্শ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন,সেখানে হযরতের ইন্তেকালের অব্যবহিত পরই জাহিলিয়াতের প্রতিবিপ্লবী শক্তির উত্তোলিত মস্তক চূর্ণ করিয়া দিয়া ইসলামী রাষ্ট্রের অস্তিত্ব রক্ষা করিয়াছেন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)। এই জন্য নবী জীবনের আলোচনা-পর্যালোচনার সঙ্গে প্রথম খলীফা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক(রা)-এর জীবনচরিত অধিকতর গুরুত্ব সহকারে আলোচনা করা আবশ্যক। বর্তমান প্রবন্ধে আমার হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর পূর্ণাঙ্গ জীবনী আলোচনা করিব না। তাঁহার গুন-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা পেশ করাই এই প্রবন্ধের একমাত্র উদ্দেশ্য।
কালের গতি-স্রোতে অতীত,বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ এমনভাবে ওতপ্রোতভাবে জড়িত যে, ইহার কোন একটি পর্যায়কে অপরটি হইতে কিছু মাত্র বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখা যায় না। যে কোন জাতির ভবিষ্যত পথ-নির্দেশের জন্য উহার অতীতকে গভীর ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পর্যালোচনা করাই সর্বাধিক উত্তম পন্থা। জাতীয় জীবনে যে ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয়, তাহা হইতে জাতিকে উদ্ধার করার জন্যও তাহার উজ্জ্বল অতীতকেই লোকদের সম্মুখে তুলিয়া ধরা আবশ্যক। রুগ্ন ব্যক্তির রোগ নির্ণয় ও নির্ধারণ এবং উহার চিকিৎসা বিধানের জন্য যেমন রোগপূর্বকালীন অবস্থা আদ্যপান্ত পর্যালোচনা করা আবশ্যক, অনুরুপভাবে জাতীয় রোগ নির্ধারণ ও চিকিৎসা বিধানের জন্য অতীত ইতিহাস আলোচনা এবং ঐতিহাসিক ব্যক্তিদের জীবন পর্যালোচনার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। বর্তমান সময়ে বিশ্বের মুসলিম জাতি অধঃপতনের চরম সীমায় উপনীত। এই মুহূর্তে হযরত আবূ বকর (রা)-এর জীবনাদর্শ নিঃসন্দেহে মুসলিম জাতির জীবন-পথের দিশারী হিসেবেই মর্যাদা পাইবে।
হযরত আবূ বকর সিদ্দীক(রা) পুরুষদের মধ্য সর্বপ্রথম হযরত মুহাম্মাদ (স)-কে সত্যিকার নবী বলিয়া বিশ্বাস স্থাপন করেন। তাঁহার এই ঈমানই উত্তরকালে তাঁহাকে ‘সিদ্দীক’ বা ‘সত্য-স্বীকারী’ উপাধিতে ভূষিত হইবার গৌরব দিয়াছে। নবুয়্যাতের দীর্ঘ তেইশ বৎসরে তিনি দ্বীন-ইসলামকে কায়েম করার প্রচেষ্টায় জান-মাল ও ইজ্জত পর্যন্ত কুরবান করিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হন নাই; বরং এই ক্ষেত্রে তিনি অপরাপর সাহাবী এবং সমস্ত মুসলমানদের অপেক্ষা অধিক অগ্রসর ছিলেন। ইস্লাম্র কবুল করার পর হইতে রাসূলে করীম (স)-এর ইন্তেকাল পর্যন্ত দীর্ঘকাল তিনি হযরতের সাহায্য-সহযোগিতা,দ্বীন-ইসলামের প্রচার ও কাফিরদের অত্যাচার-নিষ্পেষণ হইতে মুসলমানদের রক্ষা করার ব্যাপারে প্রতিনিয়ত ব্যস্ত-সমস্ত থাকতেন। রাসূলের প্রতিটি নির্দেশকে তিনি নিজের সমস্ত কাজের উপর প্রাধান্য দান করিতেন। রাসূলের জন্য তিনি নিজ জীবনেরও কোন পরোয়া করেন নাই। কাফিরদের সহিত প্রতিটি প্রত্যক্ষ সংগ্রামে তিনি রাসূলের কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া লড়াই করিয়াছেন। ঈমানের অভূতপূর্ব দৃঢ়তা ও ইস্পাত-তুল্য অনমনীয়তার পাশাপাশি তাঁহার উন্নত চরিত্র বিশ্ব-মুসলিমের জন্য এক অতুলনীয় আদর্শ। এই কারণেই তিনি ছিলেন অতীব জনপ্রিয় ব্যক্তি;তাঁহার প্রতি গোটা মুসলমানের ভালবাসা ছিল অপূর্ব।
হযরত আবূ বকর (রা)- দ্বীনী মর্যাদা এবং তাঁহার প্রতি জনগণের অসীম ভক্তি-শ্রদ্ধার কারণেই, রাসূল করীম(স) যখন রোগশয্যায় শায়িত, তখন খোদ রাসূলই তাঁহাকে নামাযে ইমামতী করার জন্য নির্দেশ দান করেন। ইহা ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ একটি ঘটনা। অতঃপর রাসূলের ইন্তেকালের পর তাঁহাকেই ইসলামী রাষ্ট্রের প্রথম খলীফা নির্বাচিত করা হয়। মুসলমানদের সাধারণ পরিষদে বিস্তারিত আলাপ-আলোচনার পর সর্বসম্মতিক্রমে তিনিই খলীফা নির্বাচিত হন। এই সময় খলীফা নির্বাচিত হইয়াই তিনি যে মূল্যবান ভাষণ দান করেন, বিশ্ব-মুসলিমের নিকট তাহা যেমন এক ঐতিহাসিক বিষয়, ইসলামী রাষ্ট্র-দর্শনের ক্ষেত্রেও উহা চিরন্তন পথ-নির্দেশক। তাঁহার এই ভাষণের পূর্ণাঙ্গ রূপ এখানে উদ্ধৃত করা যাইতেছে। তিনি সমবেত জনতাকে সম্বোধন করিয়া গুরুগম্ভীর কণ্ঠে বলেনঃ
০হে মানুষ!রাষ্ট্রনেতা হওয়ার বাসনা আমার মনে কোন দিনই জাগ্রত হয় নাই, আমি নিজে কখনও এই পদের আকাঙ্ক্ষী ছিলাম না। ইহা লাভ করার জন্য আমি নিজে আল্লাহ্র নিকট গোপনে কিংবা প্রকাশ্যে কখনও প্রার্থনাও করি নাই।
০আমি এই দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছি কেবলমাত্র এইজন্য যে, দেশে যেন কোন প্রকার বিপর্যয় সৃষ্টি হইতে না পারে।
০সরকারী ক্ষমতায় আমার মনে বিন্দুমাত্র শান্তি ও স্বস্তি নাই।
০আমার উপর এত বড় দায়িত্ব চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, আল্লাহ্র সাহায্য না পাইলে আমি তাহা সুসম্পন্ন করিতে পারিব না।
০আমাকে তোমাদের পরিচালক নিযুক্ত করা হইয়াছে,অথচ আমি তোমাদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি নহি।
০আমি যদি সোজা ও সঠিক পথে চলি, তবে তোমরা আমার সাহায্য ও সহযোগিতা করিও। আর আমি যদি ন্যায়পথ পরিত্যাগ করি, তবে তোমরা আমাকে সঠিক পথে পরিচালিত করিও।
০সত্যতা হইতেছে আমানত আর মিথ্যা বিশ্বাসঘাতকতা।
০তোমাদের মধ্যে প্রভাবহীন ব্যক্তিই আমার দৃষ্টিতে হইবে প্রভাবশালী; তাহার সকল প্রকার অধিকার আমি আদায় করিয়া দিব।
০আর যে ব্যক্তি খুবই প্রভাবশালী, আমার নিকট তাহার কোন প্রভাবই থাকিবে না, তাহার উপর দুর্বল ব্যক্তির কোন ‘হক’ থাকিলে তাহা পুরাপুরি আদায় না করিয়া আমি ক্ষান্ত হইব না।
০যে জাতির মধ্যে অন্যায়, পাপ ও নির্লজ্জতা প্রসার লাভ করে, সে জাতির উপর আল্লাহ্র আযাব নাযিল হয়।
০আমি যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ এবং তাঁহার রাসূলের আনুগত্য করিব ততক্ষণ তোমরাও আমার আনুগত্য করিবে।
০আর আমি যদি আল্লাহ্ এবং তাঁহার রাসূলের নাফরমানী করি, তবে আমার আনুগত্য করা তোমাদের কর্তব্য হইবে না।
হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) তাঁহার সংক্ষিপ্ত খিলাফতকালে ইসলামের শ্রেষ্টত্ত বিধানের জন্য যে দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা চালাইয়াছেন, বিশ্ব-মুসলিমের ইতিহাসে তাহার কোন তুলনা নাই। প্রকৃতপক্ষে তাঁহারাই খিলাফতকালে ইসলামী রাষ্ট্র-ব্যবস্থার বুনিয়াদ সুদৃঢ় হয় এবং উহা বিশ্বের বিশাল অংশে সম্প্রসারিত হয়। এই বিরাট রাষ্ট্র এশিয়ার ভারতবর্ষ ও চীন পর্যন্ত এবং আফ্রিকার মিশর,তিউনিসিয়া ও মরক্কো পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। মোটকথা, এই রাষ্ট্রই মানবীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির উৎকর্ষ সাধনের জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করিয়াছে-যাহার প্রত্যক্ষ প্রভাব দুনিয়ার শেষ মুহূর্তে পর্যন্ত অব্যাহত থাকিবে।
হযরত আবূ বকর সিদ্দীক(রা) ছিলেন রাসূলে করীম(স)-এর চিরন্তন সহচর, প্রাণ উৎসর্গীকৃত বন্ধু এবং অকৃত্রিম ও একনিষ্ঠ অনুগত। তাঁহার অন্তর ছিল অত্যন্ত দরদী। অতুলনীয় গুণ-বৈশিষ্ট্যে তিনি ছিলেন বিভূষিত।
প্রথম খলীফা নির্বাচিত হওয়ার পর ইসলামের উপর মুর্তাদ তথা ইসলাম ত্যাগকারীগণের প্রতিবিপ্লবী কর্মকাণ্ডের চরম আঘাত আসে। বস্তুতঃএই সময় ইসলামী রাষ্ট্রের সম্মুখে এক নাজুক পরিস্থিতি দেখা দেয়। কিন্তু একমাত্র আবূ বকর (রা)-এর অতুলনীয় ব্যক্তিত্বই ইসলামী রাষ্ট্রের এই অংকুরকে প্রতিবিপ্লবী কর্মকাণ্ডের আঘাত হইতে রক্ষা করিয়াছে এবং মুসলিম জনগণকে ধ্বংস ও বিপর্যয়ের কবল হইতে বাঁচাইয়াছে। তিনি পারস্য ও রোমক রাষ্ট্রসমূহের বিরুদ্ধে সৈন্য পরিচালনা করিয়া ইসলামের সমস্ত শত্রুতা অংকুরেই খতম করেন এবং ইহার পর যে রাষ্ট্র গড়িয়া উঠে,বিশ্ব-জাতিসমূহের মানসপট হইতে উহার প্রভাব আজিও মুছিয়া যায় নাই এবং কোন দিনই তাহা মুছিয়া যাইতে পারে না।
হযরত আবূ বকর (রা)-এর খিলাফত যুগের ইতিহাস বড়ই বিস্ময়-উদ্দীপক। এই ইতিহাস হইতেই তাহার বিরাট ব্যক্তিত্তের আশ্চর্যজনক দিকগুলি আমাদের সম্মুখে উজ্জ্বল হইয়া উঠে। এই মহান সত্যসেনানী গরীব ও মিসকীনের সাহায্য কাজে প্রতিনিয়ত ব্যস্ত থাকিতেন। তাঁহার দরিদ্র-সেবার নমুনা দেখিলে প্রতীয়মান হয় যে, তাঁহার ন্যায় গরীব-দরদী ভূ-পৃষ্ঠে দ্বিতীয় কেহ নাই। অপরদিকে ইসলাম প্রচার ও ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে তাঁহার বীরত্বসূচক পদক্ষেপও জীর্ণ জাতির বুকে নব জীবনের স্পন্দন জাগায়। হযরত আবূ বকর (রা)-এর সাহস, হিম্মত, দৃঢ়তা ও বিরত্তের সম্মুখে তৎকালীন দুনিয়ার সম্মিলিত শক্তিও ছিল তৃণখণ্ডের ন্যায় হীন ও নগণ্য। সংকল্প ও দৃঢ়তার এই প্রতীক প্রবর কুণ্ঠা, সংকোচ ও ইতস্ততার সহিত কিছুমাত্র পরিচিত ছিলেন না। লোকদের অন্তর্নিহিত প্রতিভা, শক্তি ও যোগ্যতা সম্পর্কে নির্ভুল ধারণা পোষণ করা এবং যোগ্যতা ও প্রতিভা অনুসারে বিভিন্ন মানুষকে বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত করা ও তদানুযায়ী তাহাদের নিকট হইতে কাজ আদায় করার ব্যাপারে তাঁহার যোগ্যতা ও দূরদৃষ্টি ছিল নিঃসন্দেহে অতুলনীয়।
রাসূলে করীম (স)- এর জিবদ্দশায় হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) একনিষ্ঠ রাসূল-প্রেমিক হিসেবেই জীবন যাপন করিয়াছেন। দুর্ধর্ষ কুরাইশগণ যখন রাসূলে করীম(স)-এর উপর নানাবিধ অমানুষিক অত্যাচার-উৎপীড়ন করিত, তখন হযরত আবূ বকর (রা)ই তাহাদের মুকাবিলায় বুক পাতিয়া দিতেন। রাসূলুল্লাহর ইসলামী দাওয়াত সর্বপ্রথম তিনিই কবুল করিয়াছেন এবং হিজরাতের কঠিন ও নাজুক অবস্থায় ‘সওর’ পর্বত-গুহা হইতে মদীনা পর্যন্ত মরু ও পর্বত-সংকুল বন্ধুর পথে পূর্ণ প্রাণোৎসর্গ সহকারে রাসূলুল্লাহর বিশ্বস্ত সহচর হিসেবে রহিয়াছেন। মদিনায় রাসূলে করীম(স)-কে ইয়াহুদীদের ষড়যন্ত্র ও মুনাফিকদের কুটিলতার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল এবং মক্কার কুরাইশ ও মদীনার ইয়াহুদীদের উপর্যুপরি শত্রুতামূলক তৎপরতার ফলে সমস্ত আরব দেশ রাসূলের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিয়াছিল। এই জটিল সময়ে হযরত আবূ বকর (রা) ই নবী করীম(স)-এর বিশেষ সহচর ও পরামর্শদাতা হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করিয়াছেন।বস্তুত ইসলামের শ্রেষ্টত্ত প্রতিষ্ঠার জন্য আবূ বকর (রা) যে ভূমিকা অবলম্বন করিয়াছেন এবং রাসূলের জীবদ্দশায় তিনি এই প্রসঙ্গে যে বিরাট খেদমত আঞ্জাম দিয়াছেন, সমষ্টিগতভাবে তাহা কেবল স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া রাখার বস্তুই নহে, উহার প্রতিটি বিষয়ে এককভাবে তাঁহার জীবনকে চিরদিনের তরে জীবন্ত করিয়া রাখার জন্য যথেষ্ট। প্রকৃতপক্ষে হযরত আবূ বকর (রা)-এর শ্রেষ্টত্ত ও মর্যাদা ভাষায় বর্ণনা করা এক সুকঠিন ব্যাপার। কেননা ইসলামের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি যে ত্যাগ ও কুরবানী দান করিয়াছেন, তাহা মূলতঃই হৃদয় ও ঈমানের ব্যাপার। তাঁহার হৃদয়ে ইসলাম ও রাসূলে করীম (স)-এর জন্য যে গভীর ভালবাসা বিদ্যমান ছিল, তাহা একমাত্র আল্লাহ্ তা’আলাই ভাল জানেন। রাসূলের ইন্তেকালের পর হযরত আবূ বকর (রা)-এর খিলাফত আমলে যে সব ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে এবং তাহাতে তিনি যে নীতি ও পদক্ষেপ গ্রহন করিয়াছেন, তাহা হইতেই প্রথম খলীফার সুতীক্ষ্ণ বিচক্ষণতা,দূরদৃষ্টি এবং গভীর ও সূক্ষ্ম জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার খলীফা নির্বাচিত হওয়ার অব্যবহিত পরই মুর্তাদগণ মাথাচাড়া দিয়ে উঠিলে তিনি অত্যন্ত দৃঢ়তাসহকারে তাহাদের মুকাবিলা করেন এবং কঠিন হস্তে বিদ্রোহীদের মস্তক চূর্ণ করিয়া দেন। অতঃপর তিনি পারস্য ও রোম সাম্রাজ্যের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। এই দুইটি রাষ্ট্রের ব্যাপারে তিনি যে সাম্যের অস্ত্র প্রয়োগ করিয়াছিলেন তার কবল হইতে আত্তরক্ষা করার মত কোন অস্ত্রই উহাদের নিকট ছিল না। পারস্য ও রোমক সাম্রাজ্যের জনগন ব্যক্তিগত তথা রাজতন্ত্রের নিষ্ঠুর পেষণে নিষ্পেষিত হইতেছিল। উভয় সাম্রাজ্যের প্রজাসাধারণ বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। বংশীয়-গোত্রীয় বৈষম্য ও পার্থক্যের অভিশাপ উভয় জাতির উপরই জগদ্দল পাথরের ন্যায় চাপিয়াছিল। শাসকগণ জনসাধারণকে নীচ বলিয়া মনে করিত এবং তাহাদিগকে সকল প্রকার মান-মর্যাদা ও অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখাই নিজেদের কর্তব্য বলিয়া মনে করিত। ঠিক এই সময়ই হযরত আবূ বকর (রা) ইসলামের বিচার,ইনসাফ ও সাম্যের পতাকা উড্ডীন করেন। তিনি পারস্য ও রোম আক্রমণকারী সেনাধ্যক্ষগণকে সুবিচার, ইনাসাফ ও সাম্যের মানদণ্ড এক মুহূর্তের তরেও হস্তচ্যুত না করার জন্য বিশেষ হেদায়েত প্রদান করেন এবং বিজিত দেশের সমস্ত জনগণের প্রতি জাতি,ধর্ম, বংশ নির্বিশেষে সাম্যের আচরণ অবলম্বন করার সুস্পষ্ট নির্দেশ দেন। ফলে যুগান্তকালব্যাপি জুলুম-পীড়ন, নির্যাতন-নিষ্পেষণ ও অসাম্য-অবিচারে জর্জরিত জনতা ইসলামের উদার সাম্য ও সুবিচার নীতির আলোকচ্ছাটায় মুগ্ধ হইয়া বাঁধভাঙ্গা বন্যার ন্যায় উচ্ছসিত হইয়া উঠে এবং উক্ত রাষ্ট্রদ্বয়ের বিরাট সামরিক শক্তি ও দুর্জয় সশস্ত্র বাহিনী বর্তমান থাকা সত্ত্বেও মুসলমানদের মুষ্টিমেয় অস্ত্র-শক্তিহীন বীর মুজাহিদীনের নিকট পরাজয় বরণ করিতে বাধ্য হয়।
রাসূলে করীম (স)-এর জীবনকাল ও খিলাফতের দ্বিতীয় পর্যায় তথা হযরত উমর (রা)-এর খিলাফত কালের মধ্যে হযরত আবূ বকর (রা)-এর খিলাফতের একটি বিরাট স্বাতন্ত্র্য ও বিশিষ্ট মর্যাদা বিদ্যমান। রাসূলের যুগ মূলত পথ-নির্দেশ ও সংশোধন সংস্কারের পর্যায়। শরীয়াতের পবিত্র বিধানসমূহ তখন নাজিল হয়। আল্লাহ্র তরফ হইতে মানবতার চিরন্তন হেদায়েতের জন্য রাসূলের মারফত ক্রমাগতভাবে আইন-কানুন নাজিল হইতেছিল। পক্ষান্তরে হযরত উমর ফারুক (রা)-এর যুগ হইতেছে সাংগঠনিক পর্যায়। তখন নব প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপনা ও যাবতীয় কার্য সম্পাদনের জন্য নিয়ম-কানুন রচিত হইতেছিল; খিলাফতের শাসন-কার্যে শৃঙ্খলা বিধানের জন্য বিভিন্ন বিভাগ গঠন করা হইতেছিল। প্রথম খলীফা হযরত আবূ বকর (রা)-এর খিলাফতকালে উল্লেখিত দুই পর্যায়ের মধ্যবর্তী হইলেও এই সময় উদ্ভুত অসাধারণ ও অস্বাভাবিক পরিস্থিতির দরুণ তাহা এক স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য সমুজ্জল।
হযরত আবূ বকর (রা)-এর খিলাফত কালে যে সব দুর্যোগ ও বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়, তাহাতে গোটা ইসলামই এক কঠিন বিপদের সম্মুখীন হইয়া পড়ে। নবী করীম (স) এর তেইশ বৎসরকালীন সাধনা ও সংগ্রামের ফলে গঠিত ঐক্যবদ্ধ জাতি এক মারাত্মক বিশৃঙ্খলার আঘাতে ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া যাইবার উপক্রম হয়। মূলতঃ রাসূলের জীবনকালে শেষ ভাগেই রাষ্ট্রীয় উচ্ছৃঙ্খলতার সূচনা হয়। মুসাইলামা বিন হাবীব নামক জনৈক ভণ্ড ইয়ামামা হইতে নবী হওয়ার দাবি করিয়া দূত মারফত অর্ধেক আরব তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়ার পয়গাম প্রেরণ করে। অতঃপর আসওয়াদ আনাসী নামক অপর এক ভণ্ডও যাদুখেলা দেখাইয়া ইয়ামনবাসীদিগকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করিতে চেষ্টা করে। এমনকি শক্তি সঞ্চয়ের পর সে ইয়ামনের দক্ষিণ অংশ হইতে রাসূলে করীম (স)-এর নিযুক্ত কর্মচারীদের বিতাড়িত করিয়া উহা নিজের শাসনাধীন করিয়া লয়। এই সময় রাসূলে করীম (স) ইয়ামনে সৈন্য প্রেরণ করিয়া তাহার মস্তক চূর্ণ করার ব্যবস্থা করিতে বাধ্য হন। বস্তুতঃআরবের জনগণ যদিও তওহীদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়া মূর্তিপূজা পরিত্যাগ করিয়াছিল; কিন্তু ইসলামের ধর্মীয় ঐক্য ও রাজনৈতিক শাসন-সংস্থার অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক সম্বন্ধে তাহাদের অনেকেই সম্পূর্ণ অবহিত ছিল না। আরববাসীগণ এমনিতেই ছিল জন্মগতভাবে স্বাধীনতাপ্রিয়; কোন প্রকার সুসংগঠিত রাষ্ট্র-সরকারের অধীনতা স্বীকার করা ও প্রাণ-মন দিয়া উহার আনুগত্য করিয়া যাওয়া তাহাদের ধাতে সহিত না। এই জন্য রাসূলের ইন্তেকালের পর মুহূর্তেই আরবের বিভিন্ন গোত্র মদীনার সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিতে শুরু করে। বিদ্রোহের আগুন তীব্র গতিতে আরবের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়ে। মুর্তাদদের পাশাপাশি অনেকে আবার বায়তুল মালে যাকাত প্রদান করিতে অস্বীকৃত জ্ঞাপন করে। মদীনায় এই সংবাদ পৌঁছিলে লোকদের মধ্যে সাংঘাতিক দুশ্চিন্তা ও অস্থিরতা দেখা দেয়। এই নাজুক পরিস্থিতিতে কি করা উচিত, তাহা তাঁহারা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। কোন কোন সাহাবী-এমনকি হযরত উমর ফারুক (রা)ও-এই মত পোষণ করিতেন যে, যাকাত অস্বীকারকারী লোকদের বিরুদ্ধে এই কঠিন মুহূর্তে কোন সশস্ত্র পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত হইবে না, বরং তাহারা যতক্ষণ পর্যন্ত কালেমায়ে তাইয়েবা ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ পড়িবে ততক্ষন তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা না করাই সমীচীন। তাঁহারা মনে করিতেন যে, বিদ্রোহীদের সঙ্গে সঙ্গে যাকাত অস্বীকারকারীদেরও দমন করার চেষ্টা করিলে যুদ্ধক্ষেত্র অধিকতর বিশাল ও ব্যাপক হইয়া পড়িবে, যাহার পরিণাম ভাল হইবে বলিয়া মনে করা যায় না। কিন্তু বীর খলীফা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)সকল প্রকার বিপদ-শঙ্কা উপেক্ষা করিয়া মুর্তাদ বিদ্রোহীদের ন্যায় যাকাত বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধেও প্রকাশ্য যুদ্ধ ঘোষণা করার সংকল্প প্রকাশ করিলেন এবং এই পদক্ষেপ হইতে তাঁহাকে কোন শক্তিই বিরত রাখিতে পারিল না।
ইসলামের ইতিহাসে মুর্তাদদের বিরুদ্ধে পরিচালিত এই যুদ্ধের গুরুত্ব খুবই অপরিসীম। বস্তুতঃএই যুদ্ধ ইসলাম ও ইসলামী রাষ্ট্রকে চির ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছে বলিলেও কিছু মাত্র অত্যুক্তি হইবে না। কেননা, একথা সুস্পষ্ট যে, মদীনার অধিকাংশ লোকের রায় অনুযায়ী হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) যদি মুর্তাদদের বিরুদ্ধে এই জিহাদ না করিতেন,তাহা হইলে ফিতনা-ফ্যাসাদ কিছুমাত্র প্রশমিত হইত না।আর এই যুদ্ধে ইসলামী ফৌজ যদি জয়যুক্ত না হইত, তাহা হইলে পরিস্থিতির অবর্ণনীয় রূপে অবনতি ঘটিত এবং উহার ফলে ইসলাম ও মুসলমান উভয়ই একেবারে ধ্বংসের সম্মুখীন হইয়া পড়িত।
এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, হযরত আবূ বকর (রা) মুর্তাদদের বিরুদ্ধে শক্তিশালী প্রতিরোধ গড়িয়া তুলিয়া অপূর্ব বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে ইহার দ্বারা তিনি বিশ্ব-ইতিহাসেরই দিক পরিবর্তন করিয়াছেন এবং নূতনভাবে মানবীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন।
মুর্তাদ বিরোধী এই জিহাদে হযরত আবূ বকর (রা) জয়ী না হইলে পারস্য ও রোমক সাম্রাজ্যদ্বয়ের মুকাবিলায় মুসলমানদের সাফল্য লাভ তো দূরের কথা, ইরাক ও সিরিয়ার দিকে মুসলমানদের অগ্রসর হওয়া পর্যন্ত সম্ভব হইত না। তখন এই বিরাট ইসলাম-বিরোধী রাষ্ট্রদ্বয়ের ধ্বংসস্তূপের উপর খৃস্টানদের সভ্যতা-সংস্কৃতির পরিবর্তে ইসলামী তাহজীব-তামাদ্দুনের প্রতিষ্ঠা কোনক্রমেই সম্ভব হইত না।
এই বিরাট জিহাদ সংগঠিত না হইলে সম্ভবতঃহযরত উমর ফারুক (রা) কুরআন মজীদকে গ্রন্থাকারে সন্নিবেশিত করার জন্য হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-কে কোন পরামর্শ দেওয়ারও প্রয়োজন বোধ করিতেন না।
পরন্তু মুর্তাদদের এই বিদ্রোহকে অংকুরেই ধ্বংস করা সম্ভব না হইলে হযরত আবূ বকর (রা) মদীনায় কোন প্রকার মজবুত রাষ্ট্র-সরকারই পরিচালনা করিতে পারিতেন না এবং তাহাঁরই পরিচালিত ইসলামী রাষ্ট্রের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর এক গগনচুম্মি প্রাসাদ তৈয়ার করা হযরত উমর (রা)-এর পক্ষে কখনই সম্ভব হইত না।
বস্তুতঃই এ বিরাট ও বিপ্লবাত্মক ঘটনাবলী মাত্র সাতাইশ মাসের এক সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে সংঘটিত হইয়াছিল। এই স্বল্পকালীন খিলাফতকে এর শ্রেণীর লোক বিশেষ গুরুত্ব দিতে চাহে না; বরং তাহারা খুলাফায়ে রাশেদুন, এমন কি ইসলামী রাষ্ট্র বলিতে দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর ফারুক (রা)-এর খিলাফতকেই বুঝিয়া থাকে এবং জনসমক্ষে উহাকেই পেশ করে। তাহারা মনে করে যে, হযরত আবূ বকর (রা) এই সংকীর্ণ সময়ের মধ্যে খুব বিরাট কোন বিপ্লবাত্মক কাজ সম্পন্ন করিতে পারেন নাই এবং তাহার সংক্ষিপ্ত কর্মকাল এইরূপ কোন কাজের জন্য যথেষ্টও নয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা মোটেই সত্য নহে। বিশ্ব-ইতিহাসের যে সব বিপ্লব মানবতার সম্মুখে উত্তরোত্তর উন্নতির দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে, উহার অধিকাংশই অতি অল্প সময়ের মধ্যে সম্পন্ন হইয়াছে। ইতিহাসে ইহার দৃষ্টান্তের কোন অভাব নাই। বিশ্ব-ইতিহাসে যে ইসলামী রাষ্ট্র-বিপ্লবের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার প্রথম ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন হযরত রাসূলে করীম (স)। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) উহাকে প্রতি-বিপ্লবী আক্রমণের আঘাত হইতে রক্ষা করিয়াছেন এবং হযরত উমর (রা) উহাকে উন্নতির উচ্চতম পর্যায়ে উন্নীত করিয়াছেন। কাজেই উমর ফারুক (রা)-এর উন্নত খিলাফত-রাষ্ট্রকে যথাযথরূপে অনুধাবন করিতে হইলে তাঁহার পূর্ববর্তী এবং নবী করীম (স)-এর পরবর্তী হযরত আবূ বকর (রা)-এর খিলাফতকাল বিস্তারিতরুপে পর্যালোচনা করা একান্তই আবশ্যক। আমরা এই দিকে পাঠকবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করিব।
হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর বৈশিষ্ট্য
বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর ইসলামী দাওয়াত ও আন্দোলনের ফলে যে ইসলামী সমাজ গঠিত হইয়াছিল, হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর পরে উক্ত সমাজের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যাক্তি ছিলেন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)। তাঁহার এই শ্রেষ্টত্ত কেবল বিশ্বনবীর জীবদ্দশায়ই সমগ্র মুসলিম সমাজের নিকট সর্ববাদিসম্মত ছিল না, তাঁহার অন্তর্ধানের পরেও গোটা মুসলিম দুনিয়ায় তিনিই ছিলেন অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠ পুরুষ। বস্তুতঃ এই বিষয়ে অতীত যুগে ইসলামী সমাজের কোন কেন্দ্রেই এবং কখনই এক বিন্দু মতবৈষম্য পরিলক্ষিত হয় নাই। এই ব্যাপারে মত বৈষম্যের কোন অবকাশও ছিল না।
কিন্তু এতৎসত্ত্বেও একথা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই যে, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর এই অবিসংবাদিত শ্রেষ্টত্তের মূলীভূত কারণ এবং তাঁহার বিশেষ গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে খুব কম লোকই অবহিত রহিয়াছেন। নবী করীম (স)-এর জীবদ্দশায় সমস্ত মুলসমানের দৃষ্টি তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হওয়ার প্রকৃত কারণ কি, তাহা মুসলিম মানসের এক অত্যন্ত জরুরী সওয়াল। অথচ একথা সর্বজনজ্ঞাত যে, ইসলামের পূর্বে আরব দেশে শ্রেষ্টত্তের মানদণ্ড হিসাবে যে কয়টি জিনিস সাধারণভাবে স্বীকৃত ছিল, তন্মধ্যে কোন একটি দিক দিয়াই হযরত আবূ বকর (রা)-এর একবিন্দু বিশেষত্ব ছিল না। তিনি কুরাইশের অভিজাত ও সমধিক মর্যাদাসম্পন্ন ‘তাইম’ গোত্রে জন্মগ্রহন করিয়াছিলেন। কিন্তু জাহিলিয়াতের যুগে সমগ্র আরব সমাজের কুরাইশ বংশের অপরাপর শাখা-প্রশাখা যতদূর সম্মান মর্যাদা লাভ করিয়াছিল, হযরত আবূ বকর (রা)-এর গোত্রটিও অনুরূপ মর্যাদার অধিকারী হইয়াছিল;উপরন্তু সুবিজ্ঞ ব্যবসায়ী হিসাবেও তাঁহার যথেষ্ট আর্থিক স্বচ্ছলতা ছিল; কিন্তু কুরাইশ বংশে তাঁহার অপেক্ষা অধিকতর ধনবান ব্যক্তি তখনো জীবিত ছিল। তাঁহার বংশ ও গোত্রের লোকদের আস্থা ও শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন তিনি। কুরাইশের জাহেলী সমাজ-ব্যবস্থায় হযরত আবূ বকর (রা) এবং তাঁহার বংশ ও গোত্রের লোক অন্যান্য লোকদের সমান শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্য কখনই লাভ করিতে পারে নাই। ইসলাম-পূর্ব যুগে বাগ্মিতা,কবিত্ব,গণকতা,নেতৃত্বের কাড়াকাড়ি প্রভৃতি দিক দিয়া হযরত আবূ বকর (রা) বিশেষ অগ্রসর ছিলেন না বলিয়া তিনি তদানীন্তন সমাজের অন্যান্য লোকদের সমপরিমাণ ইজ্জত লাভ করিতে পারেন নাই; কিন্তু তৎসত্ত্বেও কোন সব গুন-বৈশিষ্ট্য ও জনহিতকর কাজের দরুণ মানবেতিহাসের সর্বাপেক্ষা উত্তম ও পবিত্র সমাজ হযরত আবূ বকর (রা)-কে নিজেদের নেতা ও প্রথম খলিফারুপে বরণ করিয়া লইয়াছিল এবং দ্বীন ও দুনিয়ার সমগ্র ব্যাপারে তাঁহার উপর অকুণ্ঠ আস্থা স্থাপন করিয়াছিল? সাধারণভাবে ইতিহাসের প্রতিটি ছাত্র-প্রতিটি মুসলিমের পক্ষেই এই প্রশ্নটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু বর্তমানে যাঁহারা মুসলমান এবং আধুনিক বিশ্ববাসীকে ইসলামী সমাজের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অবহিত করিতে ইচ্ছুক, যাহারা নেতৃত্বের আদর্শ চরিত্র সম্পর্কে মুসলিম জনগণকে শিক্ষিত ও সজাগ করিয়া তুলিতে সচেষ্ট,তাহাদের নিকট এই প্রশ্নের গুরুত্ব অপরিসীম। বস্তুতঃইসলাম সমাজ ও ব্যক্তি গঠনের যে সর্বাঙ্গ সুন্দর আদর্শ ও মানদণ্ড উপস্থাপন করিয়াছে, তাহাই একদা কার্যকর ও বাস্তবায়িত হওয়ার ফলে হযরত আবূ বকর (রা) ও হযরত উমর (রা) প্রমুখের ন্যায় মহান নেতা লাভ করা মুসলমানদের ভাগ্যে সম্ভব হইয়াছিল।
বর্তমান প্রবন্ধে আলোচ্য প্রশ্নের জওয়াব দিতে চেষ্টা করা হইয়াছে। এই প্রবন্ধে হযরত আবূ বকর (রা)-এর চরিত্র-বৈশিষ্ট্য ও অতুলনীয় জনহিতকর কাজকর্ম সম্পর্কে আলোকপাত করা হইয়াছে। পূর্ণাঙ্গ ইসলামী সমাজে নেতৃত্বের যে শ্রেষ্ঠত্ব ও উচ্চতর মর্যাদা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর লাভ করিয়াছিলেন, তাহা লক্ষ্য করিয়াই হযরত উমর ফারুক (রা) অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক কণ্ঠে বলিয়াছিলেনঃ
শ্রেষ্ঠত্ব ও খিলাফতের সঠিক মাপকাঠি যদি ইহাই হয়, তাহা হইলে আপনার পরবর্তী খলীফাগণ তো কঠিন অসুবিধান পড়িয়া যাইবেন,কেননা আপনার সমকক্ষতা অর্জন করা কাহারো পক্ষে সম্ভব হইবে না।
পবিত্র স্বভাব-প্রকৃতি
হযরত আবূ বকর (রা)-এর জীবন চরিত আলোচনা করিলে সর্বপ্রথম আমাদের সম্মুখে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে তাঁহার হৃদয়-মনের পবিত্রতা,পরিশুদ্ধতা এবং নির্মলতা। এই কারণে ইসলাম ও নবী করীম (স)-কে সঠিক রূপে চিনিয়া লইতে তাঁহার বিশেষ কোন অসুবিধা বা বিলম্ব হয় নাই। তাঁহার সম্মুখে ইসলামের দাওয়াত ও হযরতের নবুয়্যাত পেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি উহা অকুণ্ঠিত চিত্তে গ্রহণ করিয়াছেন। কোন সংশয়, কোন দ্বিধা অথবা কোন শ্রেষ্ঠত্ববোধের জাহিলিয়াত আসিয়া এই পথে একবিন্দু প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করিতে পারে নাই। হযরত আবূ বকর (রা) তদানীন্তন সমাজের সম্মানিত ও শ্রদ্ধাভাজন লোক ছিলেন এবং একজন সম্মানিত ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির পক্ষে অপর কাহারো নেতৃত্ব মানিয়া লইতে যে পর্বত-প্রমাণ বাধার সম্মুখীন হইতে হয়, তাহা এক মনস্তাত্ত্বিক সত্য। কিন্তু হযরত আবূ বকর (রা)-কে এই ধরনের কোন বাধার সম্মুখীন হইতে হয় নাই। ইহা হইতে সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, তিনি একজন সম্মানিত ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও নেতৃত্বের অহংকার ও সম্মানের অহমিকাবোধ হইতে তাঁহার হৃদয়-মন ছিল অত্যন্ত পবিত্র।
তিনি ছিলেন স্বভাবগতভাবে অত্যন্ত সূক্ষ্মদর্শী ও সমালোচকের দৃষ্টিসম্পন্ন প্রাজ্ঞ ব্যক্তি। তাঁহার জাহিলী যুগের জীবন সাক্ষ্য প্রদান করে যে, সমালোচনার কষ্টি-পাথরে যাঁচাই-পরখ না করিয়া কোন বিষয়কে তিনি গ্রহণ করিতে কখনো প্রস্তুত ছিলেন না। কাজেই ইসলাম ও হযরতের নবুয়্যাতের প্রতি নিছক অন্ধভাবে বিশ্বাস স্থাপন করাও তাঁহার পক্ষে কিছুতেই সম্ভবপর ছিল না। এতৎসত্ত্বেও অনতিবিলম্বে ইসলাম কবুল করার একমাত্র কারণ এই যে, অসাধারণ মানসিক পবিত্রতা ও প্রকৃতির স্বচ্ছতার কারণে হযরতের সত্তবাদিতা ও তাঁহার কথাবার্তার যথার্থতা সম্পর্কে তাঁহার মন ছিল দিবালোকের মতই উজ্জ্বল ও উদ্ভাসিত। এই জন্যই ইসলামকে তিনি আপন মনের প্রতিধ্বনি হিসাবেই গ্রহণ করিয়াছেন। হযরত আবূ বকর (রা) সম্পর্কে জাহিলী সমাজের প্রভাবশালী ব্যাক্তি ইবনূদ দাগনা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঘোষণা করিয়াছিলঃ “তুমি নিকট-আত্মীয়দের হক আদায় কর, সদা সত্য কথা বল, অভাবী লোকদের অভাব পূরণ কর, আহত,নির্যাতিত ও বিপদগ্রস্ত লোকদের তুমি সাহায্য কর”-এইরূপ ব্যক্তির স্বচ্ছ হৃদয়-পটে যে কোন প্রকার মালিন্য পুঞ্জিভূত হইতে পারে না এবং রাসূলের সত্যতা স্বীকার করিতে ও ইসলাম গ্রহণ করিতে একবিন্দু বিলম্ব হইতে পারে না, তাহা বলাই বাহুল্য। এইরূপ পবিত্র আত্মা ও স্বচ্ছ মনের অধিকারীর জন্য পয়গাম্বরের দাওয়াত ও তাঁহার উজ্জ্বল মুখমণ্ডল অনেকটা মুজিজার সমতুল্য। সত্যের আওয়াজ শোনামাত্রই তাহার চৈতন্য জাগ্রত হইয়া উঠে, হৃদয় অবনমিত হয়। বিশ্বনবী নিজেই হযরত আবূ বকর (রা)-এর এই গুন –বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সাক্ষ্যদান প্রসঙ্গে স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেনঃ
আমি যাহাকেই ইসলামের দাওয়াত দিয়াছি, প্রত্যেকেই ইসলাম কবুল করার ব্যাপারে কিছু দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও সংকোচ অনুভব করিয়াছে। কিন্তু আবূ বকর বিন আবূ কোহফা ইহার ব্যতিক্রম। আমি যখনি তাঁহার সম্মুখে এই কথা পেশ করিলাম তখন উহা কবুল করিতে যেমন তাহাকে কোন প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হইতে হয় নাই, তেমনি এই ব্যাপারে তিনি বিন্দুমাত্র ইতস্ততাও বোধ করেন নাই।
হযরত আবূ বকর (রা) তাঁহার অনন্য পবিত্র স্বভাব-প্রকৃতির দরুণ অসংখ্য পবিত্র স্বভাববিশিষ্ট ও সৎকর্মশীল লোকদিগকে নিজের চতুস্পাের্শ্ব একত্রিত করিয়া লইয়াছিলেন। তাহারা আবূ বকর (রা)- এর চরিত্র-বৈশিষ্ট্য ও গুন গরিমার জন্য তাঁহার প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট ছিল। জীবনের সকল গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারেই তাঁহার সিদ্ধান্তকে তাহার অকুণ্ঠিত চিত্তে মানিয়া লইত। তাহারা যখন দেখিতে পাইল যে, হযরত আবূ বকর (রা) ইসলাম কবুল করিয়াছেন, তখন তাহারা এই বিচক্ষণ সহযাত্রী ও আস্থাভাজন নেতার সিদ্ধান্তে অনুপ্রাণিত না হইয়া পারিল না। ফলে তাহাদেরও ইসলাম কবুল করিতে বিশেষ বিলম্ব হইল না।হযরত উসমান বিন আফফান, আবদুর রহমান বিন আউফ, তালহা বিন উবাইদুল্লাহ, সায়াদ বিন আবী অক্কাস, জুবাইর বিন আওয়াম ও আবু উবাইদাহ বিন জাররাহ ন্যায় বিরাট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন লোকেরা হযরত আবূ বকর (রা)-এর দাওয়াতেই ইসলাম কবুল করিয়াছিলেন এবং এই মহান ব্যক্তিদের কারণে ইসলামী আন্দোলন প্রথম পর্যায়েই অত্যন্ত শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। ইঁহাদের এক একজন ছিলেন আপন যোগ্যতা ও কর্মক্ষমতার দিক দিয়া ইসলামের অপূর্ব সম্পদ আর এই ধরনের লোকদিগকে যে মহান ব্যক্তি ইসলামে দীক্ষিত করিয়াছিলেন, তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব ও বিরাটত্ব ভাষায় বলিয়া শেষ করা যায় না।
নৈতিক বল ও অসমসাহস
দুনিয়ায় আল্লাহ্র কালেমা প্রচার ও দ্বীন-ইসলামের পতাকা উড্ডীন করার জন্য হযরত আবূ বকর (রা)-এর নৈতিক বল ও অসম সাহসিকতা এক তুলনাহীন ব্যাপার। তিনি যে একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি এবং ব্যবসায়ী ছিলেন, তাহা সর্বজনবিদিত। একজন নেতার পক্ষে অপর কাহারো নেতৃত্ব স্বীকার করিয়া স্বীয় নেতৃত্বের পক্ষে বিপদ টানিয়া আনা অত্যন্ত কঠিন কাজ। উপরন্তু যে আন্দোলন যোগদান করার ফলে জনগণের নিকট ধিকৃত ও তিরস্কৃত হইতে হয় এবং যাহার পরিণতিতে নিজের ব্যবসায় বিনষ্ট হইতে পারে, তাহা কবুল করা দূরন্ত সাহস ও হিম্মতের উপর নির্ভর করে। কেননা তাহাতে বৈষয়িক স্বার্থ তথা রুজি-রোজগার কঠিনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে। অন্ততঃসাধারণ ও ছোট মনের ব্যবসায়ীদের খুব বেশী দ্বারা এই কাজ কিছুতেই সম্পন্ন হইতে পারে না। এ ব্যাপারে কোন ব্যবসায়ী খুব বেশী দুঃসাহসের পরিচয় দিলেও এতটুকুই তাঁহার নিকট আশা করা যাইতে পারে যে, সে নিজ পছন্দমত কোন আন্দোলনকে অন্তর দিয়া সমর্থন করিবে ও যথাসম্ভব উহাকে আর্থিক সাহায্য দান করিবে; কিন্তু নীতিগতভাবে কোন আন্দোলনকে মন-মগজ দিয়া মানিয়া লওয়া এবং কার্যতঃউহার আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রবল প্রতিকূল শক্তির সহিত সর্বাত্মক সংগ্রামে লিপ্ত হওয়া, উপরন্তু স্বীয় ব্যবসায় ও রুজী-রোজগারকে কঠিন বিপদের মুখে ঠেলিয়া দেওয়ার মত দুঃসাহস খুব কম লোকেই করিতে পারে। কিন্তু হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) এইরূপ দুঃসাহস পূর্ণমাত্রায় প্রদর্শন করিয়াছেন। অতঃপর যে সব দুঃসাহসী অভিযাত্রী এই বিপদ-সংকুল পথে পদক্ষেপ করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলেরই সম্মুখে একমাত্র আদর্শ ছিল হযরত আবূ বকর (রা)-এর অপূর্ব বিপ্লবী ভূমিকা।১ {আর্থিক কুরবানীর অনন্য দৃষ্টান্তঃইসলামের প্রতিষ্ঠা ও প্রতিরক্ষা এই উভয় কার্যেই অর্থ ব্যয় করিতে হযরত আবূ বকর (রা) ছিলেন অত্যন্ত উদারহস্ত। এই ব্যাপারে সাহাবায়ে কিরামের গোটা জামায়াতের মধ্যে তাঁহার ভূমিকা ছিল অতুলনীয়-অনুকরণীয়। রাসূলে করীম (স) যখনই কোন কাজে সাহাবাদের নিকট আর্থিক কুরবানীর আহ্বান জানাইয়াছেন, হযরত আবূ বকর (রা) তখনই সর্বোচ্চ ত্যাগের মনোভাব লইয়া আগাইয়া আসিয়াছেন। তবুক অভিযানকালে রাসূলে করীম (স) সাহাবাদের নিকট সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারের আহ্বান জানাইলে একমাত্র আবূ বকর (রা) তাঁহার সমগ্র বিত্ত-সম্পদ আল্লাহ্র রাহে দান করিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, সমগ্র বিত্ত-সম্পদ দান করিয়া দিলে তাঁহার পরিবার পরজনের ভরণপোষণ কিভাবে চলিবে? জওয়াবে তিনি বলিলেনঃ ‘তাঁহাদের জন্য আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলই যথেষ্ট’। হযরত আবূ বকর (রা) আল্লাহ্র রাহে কতখানি নিবেদিতচিত্ত ছিলেন,তাঁহার আর্থিক কুরবানীর এই অনন্য দৃষ্টান্ত হইতেই তাহা গভীরভাবে উপলব্ধি করা যায়।–সম্পাদক}
মজলুমকে সাহায্য ও সমর্থন দান
ইসলামী আন্দোলনকে প্রাথমিক পর্যায়ের কঠোর অগ্নিপরীক্ষাকালে সত্যপথের মজলুমদিগকে ইসলামের দুশমনদের নির্যাতন হইতে রক্ষা করার ব্যাপারে হযরত আবূ বকর (রা)-এর অর্থসম্পদ যে বিরাট কাজ করিয়াছে, ইতিহাসে তাঁহার দৃষ্টান্ত বিরল। বিলাল হাবশী (রা) ও ইবনে ফুহাইরা (রা)—র মত ক্রীতদাস শ্রেণীর লোক ইসলাম কবুল করার অপরাধে স্বীয় মালিক-মনিবদের অত্যাচার-নিষ্পেষণে নিতান্ত অসহায়ের মত নিষ্পেষিত হইতেছিল। হযরত আবূ বকর (রা)-এর সৌহার্দ্য ও দানশীলতার-দৌলতে তাঁহারা এই দুঃসহ আযাব হইতে নিষ্কৃতি লাভ করেন। এইজন্য তাঁহাকে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করিতে হইয়াছে। এই খাতে তাঁহাকে যে কী পরিমাণ অর্থ ব্যয় করিতে হইয়াছে, একটি ব্যাপার দ্বারাই সে সম্পর্কে অনুমান করা যাইতে পারে। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)যখন ইসলাম কবুল করেন,তখন তাঁহার নিকট চল্লিশ হাজার দিরহাম নগদ অর্থ সঞ্চিত ছিল; কিন্তু বারো-তেরো বৎসর পর যখন তিনি মদীনায় হিজরত করেন,তখন তাঁহার নিকট মাত্র পাঁচ হাজার দিরহাম অবশিষ্ট ছিল। অথচ এই দীর্ঘ সময়ে তাঁহার ব্যবসায়ে অত্যন্ত সাফল্যজনকভাবে চলিয়াছে এবং তাহাতে প্রচুর মুনাফা অর্জিত হইয়াছে।২ {রাষ্ট্রীয় তহবিলের আমানতদারীঃখিলাফতের প্রশাসনিক ক্ষমতার ন্যায় রাষ্ট্রের অর্থ-সম্পদকে হযরত আবূ বকর (রা)এক বিরাট আমানত রূপে গণ্য করিতেন। জীবিকা নির্বাহের জন্য তিনি ব্যবসা-বাণিজ্য করিতেন বলিয়া প্রথম দিকে তিনি রাষ্ট্রীয় তহবিল হইতে কোন বেতন-ভাতাই নিতেন না। কিন্তু পরবর্তীকালে খিলাফতের কার্যে সার্বক্ষণিক ব্যস্ততার ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য অচল হইয়া পড়ায় তিনি রাষ্ট্রীয় তহবিল হইতে একজন সাধারণ নাগরিকের ন্যায় নামমাত্র ভাতা গ্রহণ করিতে শুরু করেন। ইহাতে তাঁহার পরিবার-পরিজনের ভরণ-পোষণের কাজ কোন প্রকারে চলিয়া যাইত। এই পরিস্থিতিতে কিছু কিছু খাদ্য-সামগ্রী বাঁচাইয়া একদা তাঁহার স্ত্রী একটি মিষ্টি খাবার তৈয়ার করেন। খলীফা অবাক হইয়া স্ত্রীকে প্রশ্ন করিলে তিনি নিয়মিত বরাদ্দ হতে কিছু কিছু খাদ্য বাচাইবার কথা খুলিয়া বলেন। ইহা শুনিয়া খলীফা মন্তব্য করেনঃযে পরিমাণ খাদ্য বাঁচাইয়া তার মিষ্টি তৈয়ার করা হইয়াছে,উহা আমাদের না হইলেও চলে। কাজেই ভবিষ্যতে বায়তুল মাল হইতে ঐ পরিমাণ খাদ্য কম আনা হইবে। রাষ্ট্রীয় তহবিলের আমানতদারীর ব্যাপারে তিনি কতখানি সতর্ক ছিলেন, এই ঘটনা হইতেই তাহা প্রমাণিত হয়।–সম্পাদক}
হযরতের জন্য আত্মোৎসর্গ
বিশ্বনবীর ইসলামী দাওয়াত ও আন্দোলনের প্রাথমিক কাল হইতে শুরু করিয়া কঠোর বিপদ-মুসীবতের শেষ পর্যায় অবধি হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) তাঁহার জন্য আত্মোৎসর্গকৃত ও নিবেদিতচিত্ত হইয়া রহিয়াছেন। কুরাইশগণ যখনই বিশ্বনবীকে কোন প্রকার জ্বালা-যন্ত্রণা দিতে চেষ্টা করিয়াছে,হযরত আবূ বকর সিদ্দীক(রা) তখনই স্বীয় প্রাণ ও ইজ্জত বিপন্ন করিয়া তাঁহার সাহায্য-সহযোগিতায় আগাইয়া আসিয়াছেন এবং সম্মুখে অগ্রসর হইয়া প্রত্যাসন্ন বিপদের মুকাবিলা রহিয়াছেন। ইসলামী দাওয়াতের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা ও অগ্রগতির প্রত্যক্ষ আঘাতে যে সব নেতৃস্থানীয় লোকের মাতব্বরী ও নেতৃত্ব বিপন্ন হইয়াছিল, তাহারা একদিন কোন এক স্থানে একত্রিত হইয়া পারস্পরিক পরামর্শ করিতেছিল এবং আসন্ন বিপদ হইতে আত্মরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের উপায় নির্ধারণের ব্যতিব্যাস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহারা সকলেই ভয়ানক ক্রুদ্ধ,রুষ্ট ও আক্রোশান্ধ। ঠিক এই সময় নবী করীম (স) সেখানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। ইসলামের এই দুশমন লোকগুলি তাঁহার উপর হটাৎ আক্রমণ করিয়া বসিল। তাহারা বলিলঃ ‘তুমিই তো আমাদের ধর্ম ও আমাদের উপাস্য দেবতাদের তিরস্কার ও ভৎসনা কর”। নবী করীম (স) উত্তরে বলিলেন, “হ্যাঁ আমিই তাহা করি”। সহসা একটি লোক হযরতের চাদর আঁকড়াইয়া ধরিল ও তাঁহাকে কঠিন আঘাত হানার উদ্দেশ্যে হস্ত প্রসারিত করি। তৎক্ষণাৎ হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) সেখানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি ইহাদের বদমতলব বুঝিতে পারিলেন। তিনি সমস্ত বিপদের ঝুঁকি নিজের মস্তকে লইয়া সম্মুখে অগ্রসর হইলেন ও ক্রুদ্ধ স্বরে বলিয়া উঠিলেনঃ “তোমরা কি একটি লোককে শুধু এই অপরাধেই হত্যা করিতে চাও যে, সে কেবল এক আল্লাহ্কেই নিজের রব্ব বলিয়া ঘোষণা করে?”
হিজরতের কঠিন মুহূর্তে নবী করীম (স) হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-কেই সহযাত্রীরূপে গ্রহণ করিলেন। হযরতের এই সফর ছিল অত্যন্ত বিপদসংকুল এবং যে কোন মুহূর্তে তাঁহার জীবন বিপন্ন হইতে পারে-হযরত আবূ বকর (রা) ইহা ভাল করিয়াই জানিতেন। তিনি ইহাও জানিতেন যে, এই সফরে যতখানি বিপদ হযরতের উপর আসার আশংকা ছিল, তাঁহার সহযাত্রীর উপর তাহা অপেক্ষা কম বিপদ আপতিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিলনা। কিন্তু এই সবকিছু সুস্পষ্টরূপে জানিয়া বুঝিয়া লওয়ার পরও তিনি নিজের জন্য বিরাট সৌভাগ্য বলিয়া মনে করিলেন এবং এই সফরে তিনি হযরতের সঙ্গী হইয়া সকল প্রকার বিপদের মুকাবিলা করার সুযোগ পাইবেন বলিয়া আল্লাহ্র শোকরিয়া আদায় করিলেন।
মক্কা হইতে মদীনা যাওয়ার পথে এই ক্ষুদ্র কাফেলা প্রথমে আশ্রয় গ্রহণ করে ‘সাওর’ নামক পর্বত গুহায়। এই গুহায় প্রবেশ করিবার সময় হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)নবীগতপ্রাণ হওয়ার বাস্তব প্রমাণ উপস্থাপিত করেন। জনমানব বিবর্জিত শ্বাপদসংকুল পর্বত গুহায় সর্বপ্রথম হযরত আবূ বকর (রা)নিজে প্রবেশ করিয়া উহাকে পরিষ্কার করেন। উহার অসংখ্য ছিদ্রপথ বন্ধ করিয়া দেন। নবী করীম (স) এই গুহায় আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর জানুর উপর মস্তক স্থাপন করিয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন। এমন সময় একটি উন্মুক্ত ছিদ্রমুখ হইতে এক বিষধর সর্প বাহির হইয়া হযরত আবূ বকর (রা)-এর পায়ে দংশন করে। আবূ বকর (রা) বিষক্রিয়ায় জর্জরিত হইয়া পড়েন; কিন্তু হযরতের নিদ্রাভঙ্গ ও তাঁহার বিশ্রামে ব্যাঘাত সৃষ্টির ভয়ে তিনি একবিন্দু নড়াচড়া করেন নাই। কিন্তু বিষের দুঃসহ ব্যাথা তাঁহাকে এতদূর কাতর করিয়া ফেলে যে, তাঁহার চক্ষু কোটর হইতে দুই ফোঁটা অশ্রু-বিগলিত হইয়া রাসূলের গণ্ডদেশে পতিত হয়। রাসূল (স)-এর প্রতি কত অসীম ভালবাসা ও আন্তরিক ভক্তি-শ্রদ্ধা থাকার কারণে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) এইরূপ করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা ধারণা করা আমাদের পক্ষে কঠিন ব্যাপার।
কঠোরতা ও কোমলতার অপূর্ব সমন্বয়
হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর চরিত্রে কঠোরতা ও কোমলতার অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়াছিল। ইহা ছিল তাঁহার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য এবং এই কারণে তাহা ছিল নবীর প্রকৃতির সহিত গভীর সামঞ্জস্যপূর্ণ। যেখানে কঠোরতা অবলম্বনের প্রয়োজন হইত, সেখানে তিনি ঠিক প্রয়োজনীয় মাত্রায় ইস্পাতকঠিন হইয়া দাঁড়াইতেন। পক্ষান্তরে যেখানে নম্রতা প্রদর্শন আবশ্যক হইত, সেখানে তিনি অকারণ ক্রোধ ও অন্তঃসারশূন্য আত্মসম্মানবোধের মোটেই প্রশ্রয় দিতেন না। সেখানে তিনি বিগলিত-দ্রবীভূত ধাতুর মত। ফখাচ নামক এক ইয়াহুদী একবার আল্লাহ্র নাম করিয়া বিদ্রুপ করিতেছিল; ইহাতে হযরত আবূ বকর (রা)-এর দেহে প্রবল রোষাগ্নি জ্বলিয়া উঠে। তিনি পূর্ণ শক্তিতে সেই ব্যক্তিকে এক চপেটাঘাত করেন এবং বলেন, “তোমাদের ও আমাদের মধ্যে ‘যুদ্ধ নয়’ চুক্তি স্বাক্ষরিত না হইলে এখনি তোমার মস্তক ছিন্ন করিয়া দিতাম”। হুদাইবিয়ার সন্ধি-চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার সময় কুরাইশ প্রতিনিধিগণ বিদ্রুপ ও উপহাস করিয়া নবী করীম (স)-কে বলিয়াছিলেন যে, কঠিন বিপদের সময় আপনার সঙ্গীরা আপনার সহচর্য ত্যাগ করিবে। তখন হযরত আবূ বকর (রা) অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং এত কঠোর ভাষায় ইহার উত্তর দিয়াছিলেন যে, তাঁহার ন্যায় ধৈর্যশীল ব্যক্তির নিকট হইতে এইরূপ উক্তি সাধারণতঃ ধারণাও করা যায় না। কিন্তু সম্মান ও মর্যাদাবোধ তাঁহার মধ্যে এত তীক্ষ্ণ ছিল যে, ঐরুপ জওয়াব তাঁহার কণ্ঠ হইতে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই নিঃসৃত হইয়াছিল। আর যাহাকে এইরুপ কঠোর ভাষায় উত্তর দান করা হয়, জাহিলিয়াতের যুগে সে ছিল হযরত আবূ বকর (রা)-এর অনুগৃহীত। সেই কারণে লোকটি উহা সহ্য ও হজম করিতে বাধ্য হয়।
অপরদিকে বদর যুদ্ধের সময় আল্লাহ্ যখন মুসলমানদিগকে বিজয় মাল্যে ভূষিত করেন ও বহুসংখ্যক কাফির সরদার বন্দি হইয়া আসে, তখনই তিনি ইহাদের প্রতি স্নেহ-অনুগ্রহের অতল সাগর রূপে নিজেকে তুলিয়া ধরেন;অথচ একথা তিনি এক মুহূর্তের তরেও ভুলিতে পারেন নাই যে, এই সব কুরাইশ সরদারই নিরীহ ও অসহায় মুসলিমদিগকে অত্যাচার-নিষ্পেষণে জর্জরিত করিয়া তুলিয়াছিল, বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (স) এবং তাঁহার সঙ্গী সাথীদের উপর অমানুষিক অত্যাচারের ষ্টীম রোলার চালাইয়াছিল ও তাঁহাদিগকে দেশত্যাগ করিতে বাধ্য করিয়াছিল। স্বয়ং হযরত আবূ বকর (রা)ও নানাভাবে ইহাদের হাতে নির্যাতিত ও নিপীড়িত হইয়াছিলেন। কিন্তু ইসলামের জন্য এই সবকিছুই তিনি অবলীলাক্রমে বরদাশত করেন। তথাপি এই করায়ত্ত লোকদের নিকট হইতে তিনি একবিন্দু প্রতিশোধ লওয়ার কথা চিন্তা করিতে পারেন নাই। সেইজন্য অপরাপর সাহাবীদের ন্যায় তিনি বিশ্বনবীকে বন্দীদের হত্যা করার পরামর্শ না দিয়া তাহাদিগকে বিনিময় গ্রহণপূর্বক মুক্ত করিয়া দিবারই পরামর্শ দিলেন। মুসলমানদের তরফ হইতে এই অপ্রত্যাশিত অনুগ্রহ লাভ করিয়া কাফির সরদারগন হয়তবা ইসলামের দিকে আকৃষ্ট হইবে ও আল্লাহ্র সন্তোষ লাভে উদ্যোগী হইবে, ইহাই ছিল হযরত আবূ বকর (রা)-এর বিশ্বাস ও প্রত্যাশা।
দূরদৃষ্টি ও বিচক্ষণতা
হুদাইবিয়ার সন্ধি ইসলামী ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। যে পরিস্থিতিতে ও যে সব শর্তের ভিত্তিতে এই চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছিল, তাহা দৃশ্যতঃমুসলমানদের পক্ষে ছিল অত্যন্ত নৈরাশ্যব্যঞ্জক ও মর্মবিদারক। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইহার যে পরিণতি দেখা গিয়াছিল, তাহা ইসলাম ও মুসলমানদের পক্ষে শুধু বিপুল উদ্দীপকই ছিল না, প্রকৃত পক্ষে তাহা ছিল মুসলমানদের জন্য ‘ফতহুমমুবীন-সুস্পষ্ট বিজয়। এই সন্ধি চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার সময় হযরত আবূ বকর (রা)-এর ভূমিকা তাঁহার সূক্ষ্ম দূরদৃষ্টি,তীক্ষ্ণ বিচার-বুদ্ধি ও বিপুল প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের অনস্বীকার্য পরিচয় বহন করে। এই সন্ধির শর্তসমূহ একজন সাহাবীও গ্রহণ করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। হযরত উমর ফারুক (রা)সংশ্লিষ্ট শর্তসমূহের এতদূর বিরোধী ছিলেন যে, তিনি রাসূলের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া অত্যন্ত কঠোর ভাষায় কথাবার্তা বলিয়াছিলেন।(এজন্য অবশ্য আজীবন তিনি অনুতাপ করিয়াছেন)। কেবলমাত্র হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)ই এই ব্যাপারে আগাগোড়া রাসূলের সমর্থক ছিলেন। তিনি কেবল পূর্ণ শক্তিতে এই সন্ধি-চুক্তিকে সমর্থনই করেন নাই, স্বীয় প্রভাব খাটাইয়া অন্যান্য মুসলিমদেরও নিশ্চিন্ত করিয়াছিলেন। এইসব চেষ্টার ফলেই শেষ পর্যন্ত হযরত উমর ফারুক (রা)-এর অসন্তোষ প্রশমিত হয়।
বস্তুতঃযে সন্ধি চুক্তি প্রকাশ্যভাবে ও বাহ্যদৃষ্টিতে মুসলমানদের পক্ষে ক্ষতিকর ছিল-তাহাদের মর্যাদার পক্ষে ছিল হানিকর ও ভবিষ্যতের জন্য অন্ধকারের ইঙ্গিতবহ এবং যে কারণে গোটা মুসলিম সমাজের মদ্য হইতে একব্যক্তিও উহার সমর্থক ও সে সম্পর্কে নিঃসংশয় ছিল না, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) উহার সুফল প্রকাশিত হওয়ার কয়েক বৎসর পূর্বেই আপন জ্ঞানচক্ষু দ্বারা উহার সুদূরপ্রসারী কল্যাণকারিতা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। স্বয়ং নবী করীম (স) তো অহী ও ইলাহামের সাহায্যে হুদাইবিয়া সন্ধির অন্তর্নিহিত কল্যাণকারিতা ও বিরাট সুফল সম্পর্কে পূর্ণ অবহিত ছিলেন এবং এই জন্য ছিলেন দৃঢ় প্রত্যয়-অচল-অটল। কিন্তু হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)ঐরূপ সাহায্য ছাড়াই এ সম্পর্কে যে সমর্থন ও দৃঢ়টা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা বাস্তবিকই বিস্ময়কর। ইহা যদি ঈমানের স্বতঃস্ফূর্ত আলোক প্রভাব সফল হইয়া থাকে তবে বলিতেই হইবে যে, এইরূপ ঈমান-ঈমানের এই সুউচ্চতম মান একমাত্র আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এরই অর্জিত ছিল। আর রাজনৈতিক অন্তর্দৃষ্টি ও বিচক্ষণতার দৌলতে সন্ধির অন্তর্নিহিত ইতিহাসে ইহার বাস্তবিকই কোন তুলনা পাওয়া যাইবে না।
আল্লাহ্, রাসূল ও মুসলিমদের নিকট সমান প্রিয়পাত্র
হযরত আবূ বকর (রা) তাঁহার ঐকান্তিক ও নিষ্ঠাপূর্ণ খিদমতের কারণে আল্লাহ্, রাসূল ও মুসলিম জনগণের নিকট সমান প্রিয়পাত্র ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে এই জনপ্রিয়তার মর্যাদা এতদূর উন্নত ছিল যে, বিশ্বনবীর পর অন্য কেহই এই ক্ষেত্রে তাঁহার সমতুল্য ছিল কিনা সন্দেহ। ইসলামের ইতিহাসের ইহার কোন দৃষ্টান্ত খুঁজিয়া পাওয়া যায়না। এইখানে উহার কয়েকটি কারণের উল্লেখ করা যাইতেছে।
নবী করীম (স) যখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত ছিলেন,তখন লোকদের নামায পড়াইবার দায়িত্ব তিনি হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর উপর অর্পণ করেন।এ ব্যাপারে অন্যান্যদের সম্পর্কে হযরতকে যেসব পরামর্শ দেওয়া হয়,তিনি তাহা সবই অত্যন্ত দৃঢ়তা সহকারে প্রত্যাখ্যান করেন। ফলে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর উপর অর্পণ করেন। এই ব্যাপারে অন্যান্যদের সম্পর্কে হযরতকে যেসব পরামর্শ দেওয়া হয়, তিনি তাহা সবই অত্যন্ত দৃঢ়তা সহকারে প্রত্যাখ্যান করেন। ফলে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) রীতিমত নামায পড়াইতে থাকেন। একদা তিনি ঠিক সময় মসজিদে উপস্থিত হইতে পারেন নাই বলিয়া হযরত বিলাল (রা) হযরত উমর ফারুক (রা)-কে নামাযে ইমামত করিতে অনুরোধ জানান। নামাযের দেরী হওয়ার আশংকায় হযরত উমর ফারুক (রা) নামায পড়াইতে শুরু করেন। তাঁহার কণ্ঠস্বর ছিল অত্যন্ত উচ্চ ও দূরপ্রসারী। তাঁহার তকবীর ধ্বনি মসজিদ-সংলগ্ন হুজরা মুবারকে শায়িত বিশ্বনবীর কর্ণকূহরে প্রবিষ্ট হইতেই তিনি চকিত হইয়া উঠিলেন ও জিজ্ঞাসা করিলেন, আজ আবূ বকর কোথায়......... এই ব্যাপারটি না আল্লাহ্ পছন্দ করিবেন আর না মুসলিম জনগণ।
শুধু তাহাই নয়, বিশ্বনবীর দৃষ্টিতে হযরত আবূ বকর (রা)-এর যে অপূর্ব মর্যাদা ও আস্থা ছিল, তাহাও অতুলনীয়। নবী করীম (স)নিজেই তাঁহার এক বানীতে সুস্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেনঃ
সমগ্র সাহাবীর মধ্যে তাঁহার ন্যায় অনুগ্রহ আর কাহারো নাই। মানব সমাজের কাহাকেও যদি আমি বন্ধুরুপে বরণ করিতাম,তাহা হইলে আবূ বকর (রা) কেই আমার বন্ধু বানাইতাম। অবশ্য আমাদের বন্ধুত্ব,সাহচর্য্য,ভ্রাতৃত্ব ও ঈমানের দৃঢ় সম্পর্ক বিদ্যমান রহিয়াছে এবং ইহা থাকিবে ততদিন,যতদিন না আল্লাহ্ আমাদিগকে পুনরায় একত্রিত করেন।(বুখারী)
বিশ্বনবীর দরবারে হযরত আবূ বকর (রা)-এর যে কতখানি মর্যাদা ছিল, তাহা রাসূলের জীবনব্যাপী কর্মধারা হইতে সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায়। মক্কা শরীফে নবী করীম (স) প্রায়শঃহযরত আবূ বকর (রা)-এর ঘরে যাতায়াত করিতেন। মদীনা শরীফেও অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারেই তাঁহার উপস্থিতি অপরিহার্য ছিল। একদিন তিনি নিজ ঘরে তিনজন দরিদ্র সাহাবীকে খাওয়ার দাওয়াত দিয়াছিলেন;কিন্তু অধিক রাত্র পর্যন্ত তিনি রাসূলের দরবারে বিশেষ জরুরী কাজে এমনভাবে আটক ছিলেন যে, যথাসময়ে ঘরে ফিরিয়া মেহমানদারী করিতে পারেন নাই। হযরত উমর ফারুক (রা) নিজেই বলিয়াছেন যে, হযরত আবূ বকর (রা) ছিলেন বিশ্বনবীর নিত্য-সহচর। মুসলমানদের যাবতীয় সামগ্রিক ও তামাদ্দুনিক ব্যাপারে তাঁহার সাহায্য ও পরামর্শ অত্যন্ত জরুরী ছিল। অনেক গোপন বিষয় সম্পর্কেই তিনি অবহিত হইতেন। হযরতের ইন্তেকালের পূর্বে মসজিদের চৌহদ্দির মধ্যে যতগুলি দ্বার রক্ষিত ছিল,তন্মধ্যে কেবলমাত্র আবূ বকর (রা)-এর দরজা ব্যতীত আর সবই বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। নবী করীম (স)-কে কখনো অস্বাভাবিক রূপে রাগান্বিত দেখিলে সাহাবায়ে কিরাম হযরত আবূ বকর (রা)-এর মাধ্যমেই প্রকৃত ব্যাপার সম্পর্কে অবহিত হইতেন এবং প্রয়োজন হইলে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেন।
চরিত্র বৈশিষ্ট্য
হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) স্বভাবতঃই উন্নত ও মহৎ চরিত্রে বিভূষিত ছিলেন। জাহিলিয়াতের যুগেও পবিত্রতা,সততা, দয়াশীলতা, অনুগ্রহ, ন্যাপরায়ণতা ও বিশ্বাসপরায়ণতার গুণে তিনি গুণান্বিত ছিলেন। তদানীন্তন সমাজে তিনি ছিলেন একজন আমানতদার ব্যক্তি। যে সমাজে মদ্যপান,ব্যাভিচার ও ফিসক-ফুজুরী সর্বগ্রাসী রূপে ধারণ করিয়াছিল,আবূ বকর সিদ্দীক (রা)সেই সমাজের একজন মর্যাদাবান লোক হওয়া সত্ত্বেও উহার সমস্ত কলুষতা ও পঙ্কিলতা হইতে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণরূপে পবিত্র। বস্তুতঃএই গুনগুলি তাঁহার মধ্যে স্বভাবগতভাবেই বর্তমান ছিল। উত্তরকালে কুরআনের নৈতিক শিক্ষা ও হযরতের ঘনিষ্ঠ সাহচর্যের ফলে এই গুণগুলি তাঁহার চরিত্রে অধিকতর চমকিত হইয়া উঠে।
কাহারো মধ্যে তাকওয়া পূর্ণ পরিণত হইয়া উঠে তখন, যখন একদিকে তাহার মন-মগজ সকল প্রকার বাতিল চিন্তা ও মতাদর্শ হইতে মুক্ত এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সকল অন্যায় ও পাপ কাজ হইতে বিরত হয়। বিশ্বনবীর পরে এই রূপ তাকওয়া হযরত আবূ বকর (রা)-এর চরিত্রে যত প্রকটভাবে পরিলক্ষিত হয়, তত আর কাহারো মধ্যে নয়।
নেতৃত্ব,কর্তৃত্ব,মাতব্বরি,দুনিয়া-প্রীতি ও সম্মান-স্পৃহার প্রতি হযরত আবূ বকর (রা)স্বভাবতঃই ঘৃণাবোধ করিতেন। তিনি তাঁহার ধন-সম্পদ আল্লাহ্র পথে অকাতরে ও উদার-উন্মক্ত হতে ব্যয় করিয়াছেন। এমন কি খিলাফতের যুগে তিনি ছয় হাজার দিরহাম ঋণী হইয়া পড়েন। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও তিনি জনগণের একটি ক্রান্তি পরিমাণ অর্থ নিজের জন্য ব্যয় করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। তাই ইন্তেকালের পূর্বে তাঁহার নিজস্ব বাগান বিক্রয় করিয়া বায়তুলমালের ঋণ শোধ করার অসীয়াত করিয়া অর্থ উদ্ধৃত্ত যাহা কিছু থাকিলে,তাহা পরবর্তী খলীফার নিকট পাঠাইয়া দেওয়ার উপদেশ দেন।
দৃঢ়তা ও স্থিরতা
হযরত আবূ বকর (রা)-এর জীবনে সর্বাধিক কঠিন বিপদ ও অগ্নিপরিক্ষা দেখা দেয় বিশ্বনবীর ইন্তেকালের সময়।আঁ-হযরতের প্রতি তাঁহার যে দরদ ও আকর্ষণ ছিল, উহাকে ‘প্রেমের’ পর্যায়ভুক্ত বলা যাইতে পারে। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও তিনি বিশ্বনবীর ইন্তেকালের সংবাদ শ্রবণ করিয়া যে অপরিসীম ধৈর্য ও স্থৈর্যের পরিচয় দান করিয়াছিলেন, ইতিহাসে উহার তুলনা বিরল।শুধু তাহাই নয়,ইসলামের এই কঠিন মুহূর্তে হযরত আবূ বকর (রা)-এর অচল-অটল দৃঢ়তা ও প্রবল স্থিরতা যদি মুলিমদিগকে সঠিক পথ নির্দেশ না করিত,তাহা হইলে গোটা উম্মতে মুসলিমাই যে এক কঠিন ও সর্বাত্মক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হইত তাহাতে সন্দেহের লেশমাত্র নাই। বস্তুতঃআঁ-হযরতের ইন্তেকালের সংবাদ পাইয়া সর্বসাধারণ মুসলমান অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়ে,অনেকে দিগ্বিদিক জ্ঞান হারাইয়া ফেলে। হযরত উমর (রা)-এর ন্যায় বলিষ্ঠ ও পরিচ্ছন্ন দিল-দিমাগের অধিকারী লোকও এতদূর বিহবল হইয়া পড়েন যে, মসজিদে নববীতে দাঁড়াইয়া মুসলিম জনসাধারণকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বক্তৃতা করিতে লাগিলেন যে,আঁ-হযরত (স) ইন্তেকাল করেন নাই,বরং হযরত মূসা যেমন চল্লিশ দিনের জন্য আল্লাহ্র নিকট চলিয়া গিয়াছিলেন এবং পুনরায় প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন, হযরত মুহাম্মাদ(স)ও অনুরুপভাবে নিকট চলিয়া গিয়াছেন, আবার তিনি ফিরিয়া আসিবেন। এমনকি যদি কেহ বলিত যে, হযরত ইন্তেকাল করিয়াছেন,তাহা হইলে তিনি তাহাকে রীতিমত খুন করার ভীতি প্রদর্শন করিতেন এবং বলিতেন যে, নবী করীম (স) আবার ফিরিয়া আসার পর এইরূপ উক্তিকারীদের কঠিন শাস্তি দান করা হইবে।
বস্তুতঃযে কঠিন দুর্ঘটনার ফলে হযরত উমর ফারুক (রা)-এর মন-মগজে এতখানি তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছিল, তাহা অন্যান্য সাহাবীদের উপর কত দুঃসহ হইয়াছিল, উহার সঠিক ধারণা করা সম্ভব নয়। উপরন্তু বিশ্বনবীর চিরন্তন সহচর হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর উপর হযরতের ইন্তেকাল সংবাদের কি সাংঘাতিক প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে, উহার কিঞ্চিৎ হত আঁচ করা যাইতে পারে। বিশেষতঃ হযরত আবূ বকর (রা) সম্পর্কে যখন একথা জানাই আছে যে, নবী করীম (স)-এর সামান্য কষ্টেও তিনি অস্থির হইয়া পড়িতেন,তখন তাঁহার মৃত্যু সংবাদ যে তাঁহার নিকট কতখানি মর্মান্তিক হইতে পারে, তাহা ভাবিলেও শরীর শিহরিতে উঠে। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) বিশ্বনবীর মৃত্যু-সংবাদ শ্রবণ করিয়া কিভাবে ধৈর্যধারণ করেন, কিভাবে এই মর্ম-বিদারী ঘটনার মুকাবিলা করেন এবং কুরআনের আলোকে মুসলিম জনগণকে কিভাবে চরম অন্ধকার হইতে রক্ষা করেন,তাহা সত্যই বিস্ময়কর। হযরতের ইন্তেকালের মুহূর্তে আবূ বকর সিদ্দীক (রা)মদীনা শহরে উপস্থিত ছিলেন না। তিনি ছিলেন মদীনার অদূরে ‘সানাহ’ নামক স্থানে। ইন্তেকালের সংবাদ পাইয়া তিনি দ্রুত শহরে উপস্থিত হইলেন। তিনি সমস্ত মানুষকে দুঃখ-ভারাক্রান্ত ও চিন্তাক্লিষ্ট দেখিতে পাইলেন। আর দেখিলেন হযরত উমর ফারুরুক (রা)কে মসজিদে নববীতে দাঁড়াইয়া বক্তৃতা করিতে। তিনি কোথাও মুহূর্তের জন্য থামিলেন না-সোজা হযরত আয়েশা (রা) ঘরে পৌঁছিলেন ও আঁ হযরতের মুখ-মণ্ডলের আচ্ছাদন সরাইয়া চেহারা মুবারকে চুম্বন দান করিলেন। তিনি হযরতকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেনঃকত মহান পবিত্র ছিলেন জীবনে আর কত পবিত্র আজ মৃত্যুর পর! তিনি সমবেত জনতার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিলেনঃ
যাহারা হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর উপাসনা করিতেছিল তাহাদের জানিয়া রাখা আবশ্যক যে, মুহাম্মাদ (স)মরিয়া গিয়াছেন। আর যাহারা আল্লাহ্র উপাসনা-আরাধনা করিত, তাহাদের এই কথা মনে রাখিতে হইবে যে, আল্লাহ্ চিরদিনের জন্য জিন্দা ও জীবিত, তাঁহার মৃত্যু নাই।
অতঃপর তিনি কুরআন মজীদের এই আয়াত পাঠ করেনঃ
*******(আরবী)
মুহাম্মাদ রাসূল ছিলেন, অন্য কিছু নহেন। তাঁহার পূর্বে আরো অনেক রাসূল গত হইয়াছেন। তিনিও যদি মরিয়া যান কিংবা নিহত হন তবে কি তোমরা পশ্চাদপসরণ করিবে।
হযরত উমর (রা) এই আয়াত শুনিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, রাসূলের ইন্তেকাল নিঃসন্দেহ। যখনি এই অনুভূতি তাঁহার মন-মগজে তীব্রভাবে জাগিয়া উঠিল,তখনি তিনি দুঃখভারে যারপরনাই কাতর হইয়া মাটিতে ঢলিয়া পড়েন। ইহার পর তিনি ও অন্যান্য মুসলিমগণ ব্যাপারটির গভীরতা ও ব্যাপকতা এবং ইহার সুদূরপ্রসারী পরিণতি সম্পর্ককে গভীরভাবে চিন্তা করিতে শুরু করিলেন। বস্তুতঃহযরতের ইন্তেকালে গণমনে যে আঘাত লাগিয়াছিল, তাহাতে প্রায় সকলেরই চিন্তা ও বিবেচনা শক্তি লোপ পাইয়া গিয়াছিল। হযরত আবূ বকর (রা)-এর বক্তৃতার কষাঘাতে ঘনীভূত তমিস্রা অচিরেই শূন্যে বিলীন হইয়া গেল। মুসলিম মিল্লাত ইহা দ্বারা যে কত বড় কঠিন বিপদ হইতে উদ্ধার পাইয়া ছিল, তাহা সমাজ বিজ্ঞান সম্পর্কে বিন্দুমাত্র ধারণাসম্পন্ন ব্যক্তি ও উপলব্ধি করিতে পারেন।
রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি ও প্রজ্ঞা
রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি ও প্রজ্ঞায় হযরত আবূ বকর (রা)-এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য হযরতের ইন্তেকালের অব্যবহিত পরের একটি ঘটনাই যথেষ্ট। হযরত ইন্তেকাল করিয়াছেন,তাঁহার দাফন-কাফনের কাজ তখনো সম্পূর্ণ হয় নাই। ইতিমধ্যেই মদীনার আনসারগণ ‘সকীফায়ে বনী সায়েদা’য় একত্রিত হইয়া রাসূল পরবর্তী রাষ্ট্রব্যবস্থা ও খিলাফত সম্পর্কে পর্যালোচনা ও চিন্তা-ভাবনা শুরু করিয়া দিয়াছেন। এই আলোচনা ব্যাপদেশে এই প্রশ্নও মাথাচাড়া দিয়া উঠে যে, অতঃপর খিলাফতের অধিকারী কাহারা,আনসারগণ না মুহাজিরগণ?আনসারগণ নিজেদের অধিকার সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন,মুহাজিররাও কিছুমাত্র পশ্চাদপদ ছিলেন না। ফলে এমন একটা পর্যায় আসিল, যখন কেহ কেহ বলিয়া উঠিল*******(আরবী) আমাদের মধ্য হইতে একজন আমীর হইবে আর একজন আমীর হইবে তোমাদের মধ্য হইতে’। পরিস্থিতি এতদূর ঘোলাটে ও উত্তেজনাপূর্ণ হইয়া পড়ে যে, যে কোন মুহূর্তে অসংখ্য শানিত তরবারী কোষমুক্ত হইতে পারিত।
একদিকে এই কঠিন অবস্থা। অপরদিকে হযরত উমর,হযরত আবূ উবাইদাহ (রা)প্রমুখ নেতৃস্থানীয় মুহাজিরগণ মসজিদে নববীতে হযরতের ইন্তেকাল-পরবর্তী পরিস্থিতি সম্পর্কে গভীর আলোচনায় মগ্ন। এ সময় হযরত আবূ বকর (রা) হযরত আলী (রা) সমভিব্যহারে ছিলেন হযরতের কাফন-দাফনের ব্যবস্থাপনায় ব্যতিব্যস্ত। ইতিমধ্যে এক ব্যক্তি সকীফায়ে বনী সায়েদায় আয়োজিত উক্ত সম্মেলনের সংবাদ হযরত উমর ফারুক (রা)-এর নিকট পৌঁছায়। সেই সঙ্গে আনসার নেতৃবৃন্দের বক্তৃতার কথাও তাঁহাকে জানানো হয়। তিনি এই সংবাদ পাইয়া হযরত আবূ বকর (রা)কে বাহিরে ডাকিয়া পাঠাইলেন। হযরত আবূ বকর (রা)নিজের ব্যস্ততা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু যখন তাঁহাকে পরিস্থিতির গুরুত্ত সম্পর্কে অবহিত করা হইল, তখন তিনি স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন যে, অবিলম্বে পরিস্থিতি আয়ত্তাধীন না হইলে উম্মতে মুসলিমা টুকরা টুকরা হইয়া যাওয়ার পূর্ণ আশংকা রহিয়াছে। তিনি ইসলাম ও মুসলিম মিল্লাতের ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া রাসূলের দাফন-কাফনের মত গুরুত্বপূর্ণ কাজ মুলতবী রাখেন। অতঃপর মুসলিম জাতিকে আসন্ন ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করার জন্য চেষ্টা করার উদ্দেশ্য তিনি হযরত উমর ও আবূ উবাইদাহ (রা) সমভিব্যহারে সকীফায়ে বনী সায়েদায় গমন করেন।
সকীফায়ে বনী সায়েদায় পৌঁছিয়া প্রথমে তিনি সমস্ত পরিস্থিতির মূল্যায়ন এবং উহার সঠিক রূপ উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করেন। তিনি স্পষ্টত অনুভব করিতে পারেন যে, কাহারো কাহারো বক্তৃতার তীব্রতায় উপস্থিত লোকদের মন বিশেষভাবে আহত হইয়াছে। অনেকেরই মেজাজ অত্যন্ত খারাপ হইয়া গিয়াছে। এই পরিস্থিতি দর্শনেও তিনি কিছুমাত্র হতাশ হইলেন না। তিনি অবস্থা আয়ত্তে আনিতে ও লোকদের পারস্পরিক ভুল বোঝাবুঝি দূর করিতে লাগিলেন। প্রথম হযরত উমর ফারুক (রা) বক্তৃতা করিতে চাহিলে আবূ বকর সিদ্দীক (রা) তাহাকে বিরত করিলেন।কেননা তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, এই উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতিতে হযরত উমর ফারুক (রা)-এর বক্তৃতা পরিস্থিতিকে অধিকতর ঘোলাটে করিয়া তুলতে পারে। অতঃপর তিনি নিজেই দাঁড়াইয়া বক্তৃতা শুরু করিলেন। তাঁহার এই বক্তৃতা ছিল অত্যন্ত গাম্ভীর্যপূর্ণ,হৃদয়গ্রাহী,মর্মস্পর্শী ও উঁচুমানের ভাষায় অলংকারে সমৃদ্ধ। তাঁহার বক্তব্য ছিল সর্বদিক দিয়া ইনসাফ-ভিত্তিক,বিজ্ঞান ও যুক্তিমূলক। উহা উপস্থিত জনমণ্ডলীর মর্মস্পর্শ করিল, হৃদয় বিগলিত করিয়া দিল। আনসারদের কেহ কেহ এই বক্তৃতার প্রত্যুত্তর দিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু পরিস্থিতি শান্ত রাখার জন্য তাহা কিছুমাত্র সম্ভবপর ছিল না। আনসারদের সম্পর্কে প্রশংসামূলক কথাবার্তা যাহা কিছু বলা সম্ভব ছিল,তিনি তাহা সবই উত্তমরূপে বলিয়াছিলেন এবং সে সঙ্গে বিদ্যমান পরিস্থিতিতে স্বীয় দৃষ্টিকোণও অত্যন্ত অকাট্য যুক্তির ভিত্তিতে পেশ করেন। ফলে সকল কুজ্ঝটিকা,আশংকা ও সংশয়ের সকল গোলক-ধাঁধাঁ নিমেষে বিলীন হইয়া গেল। তিনি যখন দেখিলেন যে, অবস্থা শান্ত হইয়াছে, কলহ-ফাসাদের সকল ঘনঘটা শুন্য মিলাইয়া গিয়াছে, তখন তিনি একজন যোগ্যতম রাষ্ট্রনেতা হিসেবেই প্রস্তাব করিলেনঃ ‘হযরত উমর ও হযরত আবূ উবাইদাহ বিন জাররাহ (রা) তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তিদের অন্যতম, তাঁহাদের মধ্যে যাহার হাতেই ইচ্ছা তোমরা- ‘বায়’আত’ কর’।
হযরত উমর (রা)এই প্রস্তাব শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গে স্বীয় কর্তব্য স্থির করিয়া লইলেন। তিনি অপর কাহারো নাম আলোচ্য বিষয়ে পরিনত হওয়ার পূর্বেই অতীব প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব সহকারে হযরত আবূ বকর (রা)-এর দিকে হাত বাড়াইয়া দিলেন এবং বলিলেনঃ
হস্ত প্রসারিত করুন, আমরা আপনার হস্তেই ‘বায়’আত’ করিব। রাসূলে করীম (স) আপনাকেই নামাযের জন্য তাঁহার স্থলাভিষিক্ত করিয়াছিলেন। এই কারণে মুসলিম সমাজের খলিফা হওয়ার উপযুক্ত ব্যক্তি আপনিই। আমারা আপনার হস্তে ‘বায়’আত’ করিয়া প্রকৃতপক্ষে রাসূলের প্রিয় লোকদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তির হস্তেই ‘বায়’আত’ করার সুযোগ লাভ করিব।
হযরত আবূ উবাইদাহ (রা) সম্মুখে অগ্রসর হইয়া হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-কে সম্বোধন করিয়া বলিলেনঃ
সমগ্র মুজাহিদদের মধ্যে আপনিই উত্তম ব্যক্তি। সাওর-গহবরে আপনিই নবী করীম(স)-এর একক সঙ্গী ছিলেন। মুসলিমদের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ফরয হইতেছে নামায, তাহাতে আপনিই রাসূলে করীম (স)-এর প্রতিনিধি ও স্থলাভিষিক্ত। সুতরাং আপনার বর্তমানে আপনি ব্যতিত খলীফার পদাধিকারী আর কেহই হইতে পারে না।
বস্তুত মুজাহিদদের দুই শীর্ষস্থানীয় নেতা উল্লেখিত ভাষায় নিজেদের মনের কথা ব্যক্ত করায় গোটা মুসলিম উম্মতেরই প্রতিনিধিত্ব করা হইল। তাঁহারা এমন ব্যক্তিকে খলীফা নির্বাচনের প্রস্তাব ও সমর্থন করিলেন, সাম্প্রতিক সমাজে যিনি যথার্থই সর্বাধিক আস্থাভাজন, যোগ্যতাসম্পন্ন ও সর্বোত্তম ব্যক্তি। শেষ পর্যন্ত হযরত আবূ বকর (রা)জাতির গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব গ্রহনে রাযী হইলেন। উপস্থিত জনতা তাঁহার সম্মতি বুঝিতে পারিয়াই তাঁহার হস্তে ‘বায়’আত’ করার জন্য উদ্বেল হইয়া পড়ে। বস্তুতঃ ইসলামের ইতিহাসে ‘সকীফায়ে বনী সায়েদার’ এই সম্মেলন ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ সময় হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা,প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব,বিচক্ষণতা,অবিচল দৃঢ়তা এবং ইস্পাত কঠিন অনমনীয়তা প্রদর্শন না করিলে ইসলামি মিল্লাত তখনি চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইত, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নাই।
বিশ্বনবীর স্থলাভিষিক্ত হওয়ার যোগ্যতা
হযরত আবূ বকর (রা) যাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইলেন, তিনি কোন সাধারণ মানুষ ছিলেন না, তিনি ছিলেন মহান আল্লাহ্ তা’আলার সর্বোচ্চ সম্মানে ভূষিত সর্বশেষ পয়গাম্বর। আল্লাহ্ নিজেই সরাসরি অহী প্রেরণ করিয়া তাঁহাকে পথ-প্রদর্শন করিতেন। ফেরেশতাদের দ্বারা সর্বক্ষণ তাঁহার সাহায্য করিতেন। মু’জিজা দ্বারা তাঁহার প্রতিপত্তি স্থাপন করিতেন। তাঁহার চরিত্র ও যাবতীয় গুনাবলি সরাসরি আল্লাহ্র দীক্ষা ও লালনের প্রভাবে বিকশিত হইয়াছিল। এই জন্য কোন দিক দিয়াই তাঁহার মধ্যে একবিন্দু অসম্পূর্ণতা ও ত্রুটিবিচ্যুতি ছিল না; বরং তিনি ছিলেন সর্বতোভাবে বিকশিত পরিপূর্ণতার সর্বশেষ স্তরে উপনীত মানুষ। এইরূপ মহান ও বিরাট মর্যাদাসম্পন্ন অগ্রনায়কের স্থলাভিষিক্ত হওয়ার দায়িত্ব যথাযথরূপে পালন করা কিছুমাত্র সহজ কাজ নহে। নবীর সার্বিক সৌন্দর্য মাহাত্ন্য বিমুগ্ধ দৃষ্টি পরবর্তী কালের দায়িত্তসম্পন্ন ব্যক্তিকে যত কম মানের তুলাদণ্ডেই ওজন করুক না কেন, তবুও তাহা এতদূর উচ্চ ও উন্নত হইবে যে, সে তুলাদণ্ডে নিজেকে ওজন করার সাহস খুব কম লোকের মধ্যেই হইতে পারে এবং তাহাতে পুরাপুরি উত্তীর্ণ হওয়াও অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। বিশেষতঃএই ওজনকারী লোকেরা নিজেরাই যখন উচ্চ হইতেও উচ্চতর মানদণ্ডে ওজন হইবার যোগ্যতা রাখে, তখন এই কাজটি অধিকতর কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। হযরত আবূ বকর (রা) এইরুপ কঠিন মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হইয়াই মানব জাতির শ্রেষ্টতম পুরুষ ও মহান ব্যক্তিসম্পন্ন অগ্রনেতার স্থলাভিষিক্ত হইয়া ছিলেন এবং নিজের প্রথম নীতিনির্ধারক ভাষণে সুস্পষ্ট ভাষায় এই কথাই বলিয়া দিয়াছিলেন। খলীফা নির্বাচিত হওয়ার অব্যবহিত পরে প্রদত্ত তাঁহার ভাষণের প্রধান অংশ এখানে পেশ করা যাইতেছেঃ
হে জনগণ,আমাকে তোমাদের খলীফা নিযুক্ত করা হইয়াছে, অথচ আমি তোমাদের অপেক্ষা উত্তম ব্যক্তি নহি। কাজেই আমি যদি সঠিক কাজ করি, তাহা হইলে তোমরা আমার সাহায্য ও সহযোগিতা করিও। আর যদি ভুল করি, তবে আমাকে সংশোধন ও সঠিক পথানুসারি করিয়া দিবে।............ তোমাদের মধ্যে প্রতিপত্তিহীন লোক আমার নিকট হইবে প্রতিপত্তিশালী। আমি তাহাদের হক লুণ্ঠনকারীদের নিকট হইতে আদায় করিয়া দিব। পক্ষান্তরে প্রতিপত্তিশালী লোক আমার নিকট হবে প্রতিপত্তিহীন। আমি তাহাদের নিকট হইতে অপরের দ্রব্যাদি (যাহা তাহারা লুণ্ঠন করিয়া লইয়াছে) উসুল করিয়া দিব। .........আমি যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ এবং তাঁহার রাসূলের ফরমাবরদারী করিব, ততক্ষন তোমরাও আমার আনুগত্য করিবে। কিন্তু আমি যদি আল্লাহ্ এবং তাঁহার রাসূলের নাফরমানী করি, তাহা হইলে আমার আনুগত্য করা তোমাদের কর্তব্য নহে।
এই ভাষণে হযরত আবূ বকর (রা)আপন সরকারের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাতে ক্ষমতা প্রয়োগের সীমাও তিনি নির্ধারণ করিয়া দিয়াছেন। এই সীমা সামান্য মাত্র লংঘন করিলে তাঁহার সহিত কিরুপ ব্যবহার করিতে হইবে,তাহা ও নির্দেশিত করেন। সেই সঙ্গে এই মহান সত্যও তিনি উজ্জ্বল করিয়া তোলেন যে, একটি ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান ব্যক্তি হিসাবে রাসূলে করীম (স)-এর প্রদর্শিত পথে চলার জন্য তিনি সর্বতোভাবে দায়ী এবং মুসলিম জনগণ তাঁহার আনুগত্য করিয়া চলিতে ঠিক ততক্ষন পর্যন্ত বাধ্য থাকিবে, যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি নিজে আল্লাহ্র রাসূলের আনুগত্য করিয়া চলিবেন; পরন্তু তিনি ইহার একবিন্দু বরখেলাফ করিলে ইসলামী জনতা শুধু তাঁহার আনুগত্যই অস্বীকার করিতে পারিবে তাহা নহে, তাহার বিরুদ্ধে স্পষ্ট বিদ্রোহ ঘোষণা করাও তাহাদের অধিকার থাকিবে। বস্তুত নবী শ্রেষ্ঠ হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর স্থলাভিষিক্ত হওয়ার দায়িত্ব যথাযথরূপে পালন করা, সেই যুগে হযরতের কথা ও কাজের আলোকে নিজের কথা ও কাজের হিসাব মিলাইবার জন্য সাধারণভাবে সকলকে আহবান জানান সাধারণ ব্যাপার নহে। বিশেষতঃ যাহারা প্রত্যক্ষভাবেই রাসূলে করীম (স)-এর কথা ও কাজ সম্পর্কে পূর্ণরূপে ওয়াকিফহাল এবং যাহাদের মধ্যে কোন বিরাট ব্যক্তিসম্পন্ন লোকেরও সমালোচনা করার দুরন্ত সাহস ও যোগ্যতা পূর্ণ মাত্রায় বর্তমান রহিয়াছে,তাহাদের সম্মুখে উক্তরুপ চ্যালেঞ্জ পেশ করা অত্যন্ত দুঃসাহসের ব্যাপার, সন্দেহ নাই। কিন্তু হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) প্রকৃতই এই দুঃসাহস প্রদর্শন করিয়াছেন এবং তিনি যে বিশ্বনবীর স্থলাভিষিক্ত হওয়ার দায়িত্ব যতখানি পালন করা সম্ভব ততখানিই করিয়াছেন, ইতিহাসই তাহার অকাট্য সাক্ষী। ইহার সত্যতা প্রমাণের জন্য হযরত আবূ বকর (রা)-এর পরবর্তী শ্রেষ্ট মানব হযরত উমর (রা)-এর একটি বাক্য উল্লেখযোগ্য। তিনি তাঁহার (আবূ বকর সিদ্দীকের) অপূর্ব কীর্তিকলাপ দর্শনে মুগ্ধ-বিহম্বল হইয়া অত্যন্ত আফসোস মিশ্রিত কণ্ঠে বলিলেনঃ
ইসলাম ও মুসলমানদের খেদমত করার বাস্তব নমুনা ও মাপকাঠি যদি ইহাই হয় যাহা আপনি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তাহা হইলে আপনার পরবর্তী লোকদের মধ্যে আপনার সমান মর্যাদা অর্জনের হিম্মত কাহারো হইবে না।
হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) যখন খলীফা নিযুক্ত হইলেন, তখন তিনি কোন সুসংগঠিত ও সুসংবদ্ধ রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব লাভ করেন নাই। সত্য কথা এই যে, নবুয়্যাত যুগের পরে স্বয়ং তাহাকেই নূতনভাবে ইসলামী হুকুমতের গোড়া পত্তন করিতে হইয়াছে। এই জন্যই একটি নব-প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের সম্মুখে যত সমস্যা, জটিলতা ও প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হইতে পারে, উহার সবই তাঁহার সম্মুখে পর্বতসমান উঁচু হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এই সব জটিলতার সুষ্ঠু সমাধান করা সকল শাসকের পক্ষে সম্ভব হয় না। তবে আল্লাহ্র নিকট হইতে রাষ্ট্র পরিচালনার বিশেষ যোগ্যতাপ্রাপ্ত লোকেরাই ইহা সঠিকরুপে সম্পন্ন করিতে পারে। প্রথম খলীফা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) স্বভাবতই এইরুপ যোগ্যতার ধারক ছিলেন। এই কারণে বিশ্বনবীর ইন্তেকালের অব্যবহিত পরেই মুসলিম মিল্লাত যে কঠিন সমস্যাবলীর সম্মুখীন হইয়াছিল, হযরত আবূ বকর (রা) তাঁহার অপরিসীম যোগ্যতা-দক্ষতার বদৌলতে উহার সব কিছুরই সুষ্ঠু সমাধান করিয়া লইয়াছিলেন। তিনি অতি অল্প সময়ের মধ্যে যেভাবে ইসলামী রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক পর্যায়ের যাবতীয় হুমকি ও চ্যালেঞ্জের মুকাবিলা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, প্রশাসনিক বিষয়াদিতে যে অপূর্ব দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন,রাষ্ট্রপরিচালনার ইতিহাসে উহার দৃষ্টান্ত নিঃসন্দেহে বিরল। এই প্রসঙ্গে বিস্তারিত বর্ণনা করা এখানে সম্ভব নয়;তবে সংক্ষেপে কয়েকটি বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করা যাইতেছে।
(১) বিশ্বনবীর ইন্তেকালের যে প্রতিক্রিয়া আনসারদের উপর প্রতিফলিত হইয়াছিল এবং হযরত আবূ বকর (রা) যে গভীর বুদ্ধিমত্তা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের দ্বারা সমগ্র প্রতিকূল ও বিশৃঙ্খলা পরিস্থিতি আয়ত্তে আনিয়াছিলেন, ইতিপূর্বে আমরা সে বিষয়ে আলোচনা করিয়াছি। সকিফায়ে বনী সায়েদায় হযরত আবূ বকর (রা)-এর হস্তে খিলাফতের বায়’আত গ্রহণের পর যদিও আনসারদের পক্ষ হইতে কোনরূপ বিদ্রোহাত্মক পদক্ষেপের আশংকা ছিল না; কিন্তু আনসার নেতা সায়াদ-বিন-উবাদার বায়’আত গ্রহণে অস্বীকৃতির পরিণাম মারাত্মক রূপ পরিগ্রহ করিতে পারে বলিয়া মনে করা হইয়াছিল। কোন কোন লোক অনতিবিলম্বে তাঁহার সম্পর্কে নিবর্তনমূলক নীতি গ্রহণেরও পরামর্শ দিয়াছিল। কিন্তু হযরত আবূ বকর (রা) ইহাকে সাময়িক আবেগ-উচ্ছ্বাস মনে করিয়া উপেক্ষা করার নীতিই গ্রহন করেন। তিনি তখনি এই ধারণা করিয়াছিলেন যে, সায়াদের বিরুদ্ধে কোনরূপ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহন করা হইলে সমগ্র আনসার গোত্র বিক্ষুব্ধ হইয়া পড়ার আশংকা রহিয়াছে আর তাহা না করিলে কেবলমাত্র ছায়া ভিন্ন তাহার সঙ্গী আর কেহই হইবে না। হযরত আবূ বকর (রা)-এর এই চিন্তা তখনকার অবস্থায় বাহ্যতঃভুল মনে করা হইয়াছিল; কিন্তু উত্তরকালে অবস্থার গতিধারা প্রমাণ করিয়াছিল যে, হযরত আবূ বকর (রা)-এর মত-ই ছিল নির্ভুল ও সঠিক। উপরন্তু এই অবস্থায় তাঁহার সিদ্ধান্তের বিপরীতে কোন পদক্ষেপ গ্রহন করা হইলে উহার পরিণতি অত্যন্ত মারাত্মক হইত।
(২) আঁ-হযরতের ইন্তেকালের পর নবী করীম (স)-এর পরিবারের মনে হযরত আবূ বকর (রা) এবং তাঁহার হুকুমত সম্পর্কে অনেক ভুল ধারণার সৃষ্টি হইয়াছিল। উহার ফলে বেশ কিছু রাজনৈতিক জটিলতাও মাথাচাড়া দিয়া উঠিয়াছিল। রাসূল পরিবারের লোকদের সহিত মুসলিম জনগণের সম্পর্ক অত্যন্ত নাজুক আবেগময়(emotional) ও সংবেদনশীল(Sensitive)ছিল। হযরত আবূ বকর(রা) ও এই দিক দিয়া কিছুমাত্র পশ্চাদপদ ছিলেন না। কিন্তু এই সব সম্পর্কেরই ঊর্ধ্বে ছিল তাঁহার একটি বিরাট কর্তব্যবোধ, যাহার সংরক্ষণের জন্য তিনি আল্লাহ্ ও জনগণ উভয়ের নিকটই দায়ী ছিলেন। এই দ্বিমুখী ভাবধারার পারস্পরিক দ্বন্দ্বের কারণে হযরত আবূ বকর (রা)-এর যে মানসিক উদ্বেগ প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, উহা তাঁহার তৎকালীন কয়েকটি ভাষণ হইতে সুস্পষ্টরুপে বুঝিতে পারা যায়। তিনি হযরত ফাতিমা (রা), হযরত আলী(রা) ও হযরত আব্বাস (রা)-এর সহিত সাধারণ রাজনৈতিক কলা-কৌশল অবলম্বন করিতে পারিতেন না। কেননা তাহা করা হইল মুসলমানদের আবেগ-উচ্ছ্বাসের সম্পূর্ণ বিপরীত হইত বলিয়া রাজনৈতিক দৃষ্টিতেও অত্যন্ত মারাত্মক আকার ধারণ করিত। আর একজন বিচক্ষণ ও দূরদর্শী ব্যক্তি হিসাবে তিনি নিজেও তাহা কামনা করিতে পারিতেন না। অপর দিকে খিলাফত ইত্যাদির ব্যাপারে তাঁহাদের দৃষ্টিকোণ সমর্থন করাও তাঁহার পক্ষে সম্ভব ছিল না। কেননা তাহা করিলে তিনি শরীয়াতের খেলাফ করিবেন বলিয়াই তাঁহার বিশ্বাস ছিল। সর্বোপরি, রাসূল পরিবারের কোন কোন সদস্য হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর হস্তে তহন পর্যন্ত বায়’আত করেন নাই বলিয়া খিলাফতের মর্যাদা অনেকখানি ব্যাহত হইতেছিল। উপরন্তু এইরূপ পরিস্থিতিতে ইসলামের দুশমনদের পক্ষ হইতে যে কোন মুহূর্তে কঠিন বিপর্যয় সৃষ্টিরও আশংকা একেবারে কম ছিল না। এইসব কিছুই দিবালোকের মত সুস্পষ্ট ছিল;কিন্তু হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) যেমন গণ-আবেগের বিপরীত কিছু করেন নাই, তেমনি শরিয়াতের দৃষ্টিতে যে কর্মনীতি গ্রহন করা উচিত ছিল, তাহাই তিনি অবলম্বন করিয়াছেন। এই দিক দিয়া সর্বাপেক্ষা সান্তনার ব্যাপার এই ছিল যে, এই বিরোধে বনু হাশিম গোত্রের নেতা ছিলেন হযরত আলী(রা) আর তিনি কোন ব্যাপার মতবিরোধ ত করিতে পারেন; কিন্তু তাঁহার দ্বারা কোন প্রকার বিপর্যয় সৃষ্টি যে সম্ভব ছিল না, তাহা ছিল সন্দেহাতীত। ঠিক এই কারণেই হযরত আবূ বকর (রা) অসীম উদার নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন। আর তাঁহার অবলম্বিত নীতিই যে পূর্ণ মাত্রায় বিজ্ঞান-ভিত্তিক ও সত্যাশ্রয়ী ছিল, ইতিহাসই তাহার সাক্ষী।
(৩) হযরত আবূ বকর (রা) যখন খলীফা নিযুক্ত হন, তখন দেশের সার্বিক অবস্থা যারপরনাই খারাপ ছিল। বাহির হইতে রোমকদের আক্রমণের যেমন ভয় ছিল প্রতিটি মুহূর্তে, তেমনি আভ্যন্তরীণ দিক হইতে মক্কা, মদীনা ও তায়েফ ব্যতীত অবশিষ্ট প্রায় সমগ্র আরবে ইসলাম-ত্যাগ ও যাকাত অস্বীকার করার হিড়িক পড়িয়া গিয়াছিল। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন স্থানে মিথ্যা নবুয়্যাতের দাবিদার ও ধন-সম্পত্তির লোভী ব্যক্তিরাও মাথাচাড়া দিয়া উঠে। দেখিতে দেখিতে ইহাদের সমর্থক সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইতে থাকে। অপরদিকে তাবুক ও মূতা’র যুদ্ধ মুসলমান ও রোমকদের মধ্যে এক অন্তহীন সংঘাতের সূচনা করে। রোমকগণ প্রতি মুহূর্তেই মুসলমানদের উপর আক্রমন-উদ্যত হইয়াছিল;মুতা’র যুদ্ধে মুসলমানদের পশ্চাদপসারণের কারণে তাহাদের হিম্মত অধিকতর বৃদ্ধি পায়। এইরূপ অবস্থায় খিলাফতের আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা এবং দেশের প্রধান অঞ্চলসমূহে বিদ্রোহের অগ্নুৎগীরণের সংবাদ প্রচারিত হইলে তাহারা অনতিবিলম্বেই যে মদীনার উপর আক্রমন করিতে পারে, তাহা ছিল এক সাধারণ সত্য কথা। মূলতঃএই দুইটি বিপদ ছিল পূর্ব হইতেই বর্তমান এবং হযরত আবূ বকর (রা)-এর খলীফা নিযুক্তির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে এই উভয় বিপদের সহিত মুকাবিলা করিতে হইয়াছে। এই পরিস্থিতিতেকি অসাধারণ সাহস-হিম্মত ও কি অপূর্ব বুদ্ধি-বিবেচনা সহকারে বিপ দুইটির মুকাবিলা করিয়া তিনি বিপুলভাবে জয়লাভ করেন, তাহা সহজেই উপলব্ধি করা যায়।।
তিনি খলীফা নিযুক্ত হইয়াই সর্বপ্রথম রোমকদের উপর আক্রমণের জন্য প্রস্তুত সৈন্যবাহিনীকে রওয়ানা করাইয়া দিলেন। বস্তুতঃহযরত নবী করীম (স)-এর জীবদ্দশায়ই এই বাহিনীকে হযরত উসামা বিন জায়েদের নেতৃত্বে প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়; কিন্তু হযরতের আকস্মিক রোগাক্রান্ত হইয়া পড়ার কারণে তখনকার মত যাত্রা স্থগিত রাখা হয়। হযরতের ইন্তেকালের পর এই বাহিনী প্রেরণের ব্যাপারে বিপুল সংখ্যক সাহাবী বিপরীত মত পোষণ করিতে শুরু করেন। কেহ কেহ বিদ্যমান আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক দিক দিয়া অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতিতে এইরূপ বাহিনীকে রাজধানীর বাহিরে প্রেরণ করা অদূরদর্শীতার কাজ হইবে বলিয়া যুক্তি প্রদর্শন করে। কাহারও পক্ষ হইতে আবার ক্রীতদাস বংশজাত হযরত উসামার অধিনায়কত্ব সম্পর্কেও আপত্তি উত্থাপন করা হয়। কিন্তু হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) এই সব বাধা-বিপত্তি ও প্রতিকূল পরিস্থিতিতে অবিচলভাবে স্বীয় নীতিতে দণ্ডায়মান রহিলেন। তিনি স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করিলেনঃ ‘যে ঝাণ্ডা রাসূলে করীম নিজে উন্নত করিয়াছেন, আমি তাহা অবনমিত করিতে পারিব না’। তিনি বিরোধী মত পোষণকারীদের প্রস্তাবের জওয়াবে বলিলেনঃ ‘কুকুর ও শৃগালও যদি আমাকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলে,তবুও আমি রাসূলের পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত বাতিল করিতে পারিব না। রাসূল যাহাকে নিযুক্ত করিয়াছেন, আমি তাহাকে কিরূপে পদচ্যুত করিব।
মোটকথা, এইসব বাধা-বিপত্তি ও প্রতিকূল পরিস্থিতি সত্ত্বেও হযরত আবূ বকর (রা) হযরত উসামার নেতৃত্বে সৈন্যবাহিনী রওয়ানা করাইয়াই ছাড়িলেন। বস্তুতঃখলিফাতুল মু’মিনীনের এই অপরিসীম দৃঢ়তা ও মনোবলের ফলেই আল্লাহ্র অসীম রহমত নাজিল হয়। উসামার নেতৃত্বে প্রেরিত সৈন্যবাহিনী বিপুল শান-শওকতপূর্ণ জয়লাভ করিয়া মদীনায় প্রত্যাবর্তন করে। ইহার ফলে আভ্যন্তরীণ দুশমনগণ অত্যন্ত বিস্মিত ও সন্ত্রস্ত হইয়া পড়ে এবং বৈদেশিক শত্রুগণও হইয়া পড়ে অত্যন্ত ভীত ও শঙ্কিত। আরবের বিদ্রোহী গোত্রসমূহ যখনরোমকদের বিরুদ্ধে এই সৈন্য প্রেরণের সংবাদ শুনিতে পাইল, তখন তাহারা মদীনাকেন্দ্রিক রাষ্ট্রের অন্তর্নিহিত বিরাট শক্তির পরিচয় পাইয়া প্রকম্পিত না হইয়া পারিল না।। অপর দিকে হিরাকল স্বীয় রাষ্ট্রের সীমান্ত সংরক্ষণের জন্য অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল।এক কথায়, হযরত আবূ বকর (রা) একই প্রস্তর নিক্ষেপে দুইটি শিকার করিলেন এবং একথা অনস্বীকার্য যে, তাঁহার এই পরিকল্পনা পূর্ণমাত্রায় সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল।
বহিরাক্রমণের বিপদ দূরীভূত হওয়ার পর অবশিষ্ট শক্তি প্রয়োগ করিয়া হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) অত্যন্ত দৃঢ়তা সহকারে আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ-প্রতিবিপ্লব চূর্ণ করিয়া দেন-যদিও সাহাবীদের এক প্রভাবশালী দলের কিছু লোক এই ব্যাপারে উদার নীতি পোষণ করা ও কঠোরতা অবলম্বন না করারই পক্ষে মত পোষণ করিতেন। তাঁহারা বলিতেনঃযাহারা নিজদিগকে মুসলমান বলিয়া পরিচয় দেয়, তাহারা শুধু যাকাত দিতে অস্বীকার করে বলিয়াই তাহাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র প্রয়োগ করা ও জানমালের হেফাজত হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত করা উচিত হইবে না। কিন্তু হযরত আবূ বকর (রা) তাঁহাদের এই দৃষ্টিকোণ কিছুতেই সমর্থন করিতে পারিলেন না। তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলিলেনঃইসলামে নামায ও যাকাত সমপর্যায়ভুক্ত ইবাদত, কাজেই নামায কায়েমের জন্য যদি যুদ্ধ করা যায় তাহা হইলে যাকাত অনাদায়কারীদের বিরুদ্ধে কেন লড়াই করা যাইবে না?তিনি ঘোষণা করিলেনঃ ‘আল্লাহ্র শপথ, যাহারাই নামায ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্যের সৃষ্টি করিবে (নামায পড়িবে ও যাকাত দিবেনা), রাসূলের যুগে যে সব জিনিসের যাকাত দেওয়া হইত তাঁহার একটি রশিও আজ দিতে যাহারা অস্বীকার করিবে,আমি তাহাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করিব। ‘তিনি আরো বলিলেনঃ ‘এই জিহাদে যদি কেহই আমার সঙ্গী না হয়, তবুও আমি একাকীই লড়াই করিব’।
হযরত আবূ বকর (রা)-এর এই নিরাপোষ ও অনমনীয় মনোভাবের ফলেই সমগ্র মুসলমানের হৃদয়ে নবতর কর্মপ্রেরণা ও উদ্দীপনার সৃষ্টি হয় এবং অত্যল্প কালের মধ্যেই খিলাফত-রাজ্য হইতে সকল প্রকার বিদ্রোহ-প্রতি বিপ্লব মূলোৎপাটিত হয়। এই প্রসঙ্গে সর্বাপেক্ষা স্মরণীয় ব্যাপার এই যে, বিদ্রোহের পরিধির অত্যন্ত ব্যাপক আকার ধারণ, মদীনীয় সরকারের চারদিকে বহুবিধ জটিল সমস্যার পরিবেষ্টন এবং সর্বোপরি বিদ্রোহীদের প্রতি বিপুল সংখ্যক আপন লোকদের উদার নীতি অবলম্বনের পক্ষপাতী হওয়া সত্ত্বেও হযরত আবূ বকর (রা) এক বিন্দু দমিত হন নাই, বরং সমঝোতা ও উদার নীতি গ্রহণের সকল প্রস্তাবই তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। কতখানি আত্মবিশ্বাস ও আল্লাহ্র প্রতি নিঃশংক ভরসা থাকিলে এই রূপ সাংঘাতিক পদক্ষেপ গ্রহন করা যাইতে পারে, তাহা সুধীমাত্রেই অনুভব করিতে পারেন।বস্তুত এহেন সংকটপূর্ণ মুহূর্তে হযরত আবূ বকর (রা) যদি এইরূপ অটল মনোভাবের পরিচয় না দিতেন বরং ক্রমবর্ধমান বিদ্রোহ-প্রতিবিপ্লবে ভীত শঙ্কিত হইয়া বিদ্রোহী ও ইসলাম-ত্যাগীদের সম্মুখে অস্ত্র সংবরণ করিতেন, তাহা হইলে ইসলামী রাষ্ট্র-ব্যবস্থার নাম পর্যন্ত ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে মুছিয়া যাইত, তাহাতে একবিন্দু সন্দেহ থাকিতে পারে না। আর তাহাই যদি হইত-তাহা হইলে বিশ্ব-সভ্যতার ইতিহাস আজ সম্পূর্ণ বিপরীতভাবে লিখিত হইত;বরং বিশ্ব-সভ্যতার গতিই স্তদ্ধ হইয়া যাইতে বাধ্য হইত, তাহা সন্দেহাতীত। হযরত আবূ বকর (রা)-এর এই কঠোরভাবে ভূমিকা ও অনমনীয় আদর্শবাদী পদক্ষেপের ফলে ইসলামী সভ্যতায় যে প্রবল জোয়ার আসিয়াছিল, মাত্র সোয়া দুই বৎসরের শাসনকালেই তাহা সমগ্র আরব দেশকে পরিপ্লাবিত করিয়া এবং প্রতিবেশী ইরাক রাজ্যকে পরিসিক্ত করিয়া ও অন্যান্য দেশের উপর হইতে প্রবাহিত হইতে শুরু করিয়াছিল। একটি নবতর সভ্যতার এত আকস্মিক ও সল্পসময়ের মধ্যে এইরূপ ব্যাপকতা,সম্প্রসারণ ও অগ্রগতি লাভের কোন দৃষ্টান্তই বিশ্ব-ইতিহাসে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।
বস্তুতঃহযরত আবূ বকর (রা)-এর নায় মহান চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তি যখন কোন রাষ্ট্রের পরিচালক হয় তখনই সেই রাষ্ট্রের অধিবাসী কোটি জনগণের উন্নতি ও সার্বিক কল্যাণই শুধু নয়, ইসলামেরও সমৃদ্ধি ও প্রতিপত্তি অর্জন সম্ভব হইতে পারে।
হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর খিলাফত
প্রথম খলীফা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর মহান জীবন বহু উজ্জ্বল কীর্তিকলাপে পরিপূর্ণ। বিশেষতঃ তাঁহার সোয়া দুই বৎসরের স্বল্প মিয়াদী খিলাফত আমলে চেষ্টা-সাধনার যে গগনস্পর্শী পিরামিড রচিত হইয়াছে, তাহা কিয়ামত পর্যন্ত অক্ষয় ও অম্লান হইয়া থাকিবে। বিশ্বনবীর ইন্তেকালের অব্যবহিত পরই জাহিলিয়াতের সূচিভেদ্য অন্ধকারে গোটা আরব দেশ-তথা ইসলাম জগত আচ্ছন্ন হইবার উপক্রম হয়। বহু প্রধান ও প্রভাবশালী গোত্র ইসলামী হুকুমতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। নবুয়্যাতের মিথ্যা দাবিদারগণ বিভিন্ন অঞ্চলে বিদ্রোহের পতাকা উড্ডীন করে। যাকাত দিতে অস্বীকারকারীরা শুধু যাকাত দান হইতেই বিরত থাকে নাই, দারুল-খিলাফত মদীনা মুনাওয়ারাকেও লুণ্ঠন করিবার জন্য হুঙ্কার ছাড়ে। এককথায় বলা যায়, ইসলামের প্রচণ্ড মার্তণ্ড অস্তগামী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আকস্মাৎ উহার প্রদীপ্ত দীপশিখা শেষরাত্রের তৈলহীন প্রদীপের ন্যায় নির্বাণোন্মুখ হইয়া পড়ে। কিন্তু রাসূলের স্থলাভিষিক্ত ও মহান খলীফার দূরদৃষ্টি,সাহসিকতাপূর্ণ মনোবল, রাজনৈতিক সূক্ষ্মবুদ্ধি ও অসাধারণ ধৈর্য-স্থৈর্যের ফলে ইসলামের চেরাগ শুধু চির নির্বাণের কবল হইতেই রক্ষা পায় নাই, হেদায়েতের সেই উজ্জ্বল মশাল দ্বারা সমগ্র আরবকে উদ্ভাসিত করিয়া তোলে। এইজন্যই বলিতে হয় যে, বিশ্বনবীর অন্তর্ধানের পর যে মহান ব্যক্তি ইসলামী জীবন ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠাকে ধ্বংসের কবল হইতে রক্ষা করিয়াছেন এবং মুসলিম জাহানের উপর যাহার অপরিশোধ্য ঋণ রহিয়াছে, তিনি হইতেছেন প্রথম খলীফা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)।
দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর ফারুক (রা)-এর খিলাফতকালে অনেক বড় বড় কীর্তি-কাণ্ড সম্পাদিত হইয়াছে, বহুতর কঠিন ও জটিল বিষয়ের সুমীমাংসা হইয়াছে। এমন কি রোমক ও ইরানের বিশাল সাম্রাজ্য পর্যন্ত ইসলামী সয়লাবের আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে। ইহা সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক সত্য, যাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। কিন্তু ইসলামী খিলাফতের বুনিয়াদ সংরক্ষণ, সমগ্র ইসলামী উম্মাহর হৃদয়মনে অপ্রতিরোধ্য বিপ্লব ও আত্মোৎসর্গের প্রচণ্ড ভাবধারার জাগরণ, খিলাফতে ইলাহীয়ার সংগঠন-সংযোজন ও শৃঙ্খলা স্থাপন কাহার দ্বারা সম্ভব হইয়াছে? সর্বোপরি ধ্বংসের ঝঞ্জা-বাত্যা হইতে ইসলামী সমাজ-রাষ্ট্রকে কে বাঁচাইয়াছে?- এইসব প্রশ্নের জওয়াবে কেবলমাত্র আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর নামই উচ্চারণ করা যাইতে পারে। আলোচ্য প্রবন্ধে আমরা আবূ বকর সিদ্দীক (রা) এর খিলাফতকালের কার্যকলাপ ও ইসলামের আকাশস্পর্শী বিস্তারের যাচাই ও পর্যালোচনা উপস্থাপনের চেষ্টা করিব।
খিলাফতের পরামর্শ-ভিত্তিক চরিত্র
একথা অনস্বীকার্য যে, নবুয়্যাতের আদর্শে ইসলামী খিলাফতের প্রথম ভিত্তি স্থাপন করেন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)। প্রথমতঃতাঁহার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় প্রকাশ্য জনমতের ভিত্তিতে। পরন্তু তিনি যতগুলি প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করিয়াছেন,উহার প্রত্যেকটির পশ্চাতেই ইসলামী নাগরিক-জনতার আস্থাভাজন ও স্বাভাবিক প্রতিনিধি মর্যাদাসম্পন্ন শ্রেষ্ট সাহাবিগণকে স্বতঃস্ফূর্ত রায় বর্তমান ছিল। এই জন্য তিনি উপরোক্ত শ্রেণীর সাহাবিগণকে দারুল খিলাফত হইতে দূরে যাইবার অনুমতি দান করেন নাই কখনও। রাসূলে করীম (স) উসামা বাহিনীর সহিত যাইবার জন্য হযরত উমর ফারুক (রা)-এর নাম তালিকাভুক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রথম খলীফা এতদপেক্ষাও অধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য তাঁহাকে মদীনার বাহিরে যাইবার অনুমতি দেন নাই; উসামার নিকট হইতে ইহার অনুমতি তিনি নিজেই গ্রহন করিয়াছিলেন।
সিরিয়া আক্রমণের প্রয়োজন দেখা দিলে বিষয়টিকে তিনি প্রথমে সাহাবাদের বিশিষ্ট জামায়াতের নিকট পরামর্শের জন্য পেশ করেন। বিস্তারিত আলোচনার পর হযরত আলী (রা)-এর একটি প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে জিহাদ-ঘোষণা করার ব্যাপারেও অনুরুপভাবে পরামর্শ গ্রহন করা হয়। অবশ্য একথাও সত্য যে, উমর ফারুক (রা)-এর খিলাফতকালের ন্যায় তখন মজলিসে শুরা সুষ্ঠুরুপে গঠিত ছিলনা; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও কোন জাতীয় রাষ্ট্রীয় ও দ্বীনী গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে বিশিষ্ট সাহাবীদের মত ও রায় গ্রহণে কোন সময়ই অবহেলা করা হয় নাই।
আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা ব্যবস্থা
রাষ্ট্রের স্বরূপ ও ধরণ নির্ধারণের পর দেশের আভ্যন্তরীণ শাসন-শৃঙ্খলা উন্নততর করা এবং গুরুত্বপূর্ণ পদসমূহ বণ্টন ও পদাধিকারীদের সুষ্ঠু নির্বাচন অত্যন্ত জরুরী কাজ। হযরত আবূ বকর (রা)-এর খিলাফতকালে দেশজয় বা রাজ্য বিস্তারের কেবলমাত্র সূচনা হইয়াছিল; কাজেই তাঁহার খিলাফতকে কেবল আরব উপদ্বীপ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ মনে করিতে হইবে। তিনি আরব উপদ্বীপকে কয়েকটি প্রদেশ ও জেলায় বিভক্ত করিয়াছিলেন। মদীনা, মক্কা, তায়েফ, সানয়া,নাজরান, হাযরামওত,বাহরাইন ও দওমাতুল জান্দাল প্রভৃতি স্বতন্ত্র প্রদেশ ছিল। প্রত্যেক প্রদেশেই একজন করিয়া কর্মাধ্যক্ষ(আজিকার ভাষায় গভর্নর) নিযুক্ত ছিলেন।সকল প্রকার রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন তাঁহার কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। দারুল খিলাফতেও প্রত্যেক বিভাগেরই একজন করিয়া প্রধান নিযুক্ত ছিলেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে, হযরত আবূ উবাইদা (রা) সিরিয়ায় সেনাপতি নিযুক্ত হওয়ার পূর্বে অর্থ উজীর পদে অভিষিক্ত ছিলেন, হযরত উমর (রা)ছিলেন বিচারপতি আর হযরত উসমান ও হযরত জায়দ বিন সাবেত (রা) খিলাফত-দরবারের সেক্রেটারি পর্যায়ের কর্মকর্তা ছিলেন।
শাসনকর্তা ও অফিসার নির্বাচনে হযরত আবূ বকর (রা) সব সময়ই নবী করীম (স)-এর যুগের অনুরূপ পদাধিকারী লোকদের প্রাধান্য দিতেন এবং যিনি পূর্বে যে কাজ করিয়াছেন, তাঁহার দ্বারা সেই কাজ লইতে চেষ্টা করিতেন।ফলে তাঁহাকে প্রায় কোন বিভাগেই অযোগ্য ও অনভিজ্ঞ লোক নিয়োগজনিত অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হয় নাই।
হযরত আবূ বকর (রা) একজনকে যখন কোন দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত করিতেন, তখন সাধারণতঃ তাঁহাকে উপস্থিত করিয়া তাঁহার দায়িত্ব ও কর্তব্য বিস্তারিতভাবে বুঝাইয়া দিতেন এবং অত্যন্ত প্রভাবশীল ও মর্মস্পর্শী ভাষায় তাকওয়া,ন্যায়নীতি ও সর্বক্ষেত্রে সুবিচার অবলম্বনের জন্য উপদেশ দান করিতেন। এখানে আমর-বিন আস ও অলীদ বিন আকাবা (রা)-কে যাকাত আদায়কারী নিয়োগকালীন প্রদত্ত উপদেশের অংশ-বিশেষ উল্লেখ করা যাইতেছেঃ
প্রকাশ্যে ও একাকীত্বে আল্লাহ্কে ভয় কর। আল্লাহ্কে যে ভয় করে, আল্লাহ্ তাহার জন্য এমন একটি পথ ও রিযিক লাভের এমন উপায় সৃষ্টি করিয়া দেন,যাহা কাহারও ধারণায় আসিতে পারে না। আল্লাহ্কে যে ভয় করে, আল্লাহ্ তাহার গুনাহ মাফ করিয়া দেন এবং তাহার নেক কাজের ফল দ্বিগুণ ও ততোধিক পরিমাণ দান করেন। জনগণের কল্যাণ কামনা ও খেদমত নিঃসন্দেহে উত্তম তাকওয়ার কাজ।
এমন গুরুত্বপূর্ণ পথে তোমরা অগ্রসর হইতেছ, যেখানে দ্বীনের প্রতিষ্ঠা ও খিলাফতের দৃঢ়তা সাধনের ব্যাপারে বিন্দুমাত্র গাফেলতি বা আতিশয্য ও অবহেলার কোনই অবকাশ নাই। কাজেই অবসাদ ও উপেক্ষার কদর্য অভ্যাস পরিত্যাগ কর।
ইয়াজিদ বিন সুফিয়ানকে সিরিয়ার শাসনকর্তা নিযুক্তির সময় তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেনঃ
হে ইয়াজিদ! তোমার বহু সংখ্যক নিকটাত্মীয় রহিয়াছে;তোমার রাষ্ট্রক্ষমতার দ্বারা তাহাদিগকে অনেক স্বার্থোদ্ধারের সুযোগ করিয়া দিতে পার। কিন্তু জানিয়া লইও, ইহাই আমার সবচেয়ে বড় ভয়। নবী করীম (স) ইরশাদ করিয়াছেনঃ
মুসলমানদের শাসনকর্তা যদি কাহাকেও বিনা অধিকারে শুধুমাত্র প্রীতি হিসাবে মুসলমানদের উপর কর্তৃত্বসম্পন্ন অফিসার নিযুক্ত করে, তবে তাহার উপর আল্লাহ্র অভিশাপ বর্ষিত হয়। আল্লাহ্ তাহার কোন ওযর কিংবা প্রায়শ্চিত্ত কবুল করেন না। এমন কি শেষ পর্যন্ত থাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করিবেন।
শাসকদের প্রতি কড়া দৃষ্টি
সরকারের আইন-কানুন যতই উত্তমভাবে রচিত ও বিধিবদ্ধ হউক না কেন, কিন্তু দায়িত্তসম্পন্ন শাসকদের উপর যদি কড়া দৃষ্টি রাখা না হয় এবং জনগণের তীক্ষ্ণ সমালোচনার সুষ্ঠু ও অবাধ ব্যবস্থা না থাকে, তাহা হইলে গোটা শাসন ব্যবস্থা চূর্ণ-বিচূর্ণ ও কর্তৃপক্ষের প্রতি জনগণের স্বাভাবিক আশা-আকাঙ্ক্ষা ব্যর্থ হইতে বাধ্য। এই কারণেই প্রথম খলীফার স্বাভাবিক বিনয়, নম্রতা, ক্ষমাশীলতা, সহিষ্ণুতা ইত্যাদি মহৎ গুনাবলী থাকা সত্ত্বেও স্থান বিশেষে তাঁহাকে বিশেষ কঠোরতা,পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও তীব্র সমালোচনার মাধ্যমে খাঁটি, ভেজাল ও সদাসদ নির্ণয়ের দুঃসাধ্য কাজ করিতে হইয়াছে। ব্যক্তিগত ব্যাপারসমূহে অতিশয় নম্রতা ও বন্ধুতাবলম্বনই ছিল তাঁহার স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য; কিন্তু সেই সঙ্গে দ্বীনী, প্রশাসনিক ও খিলাফত সংক্রান্ত ব্যাপারে তিনি বিন্দুমাত্র ত্রুতি-অবহেলা বরদাশত করিতেন না। এই কারণে শাসনকর্তাদের মধ্যে যখনি কোন অবাঞ্ছনীয় ত্রুটি পরিলক্ষিত হইত, তখন অত্যন্ত কঠোরতা অবলম্বন করিয়াই তিনি উহার শাস্তি বিধান করিতেন।
দণ্ড বিধানে নম্রতা
হযরত আবূ বকর (রা) ব্যক্তিগতভাবে অপরাধীদের প্রতি অতিশয় নম্র ও সহানুভূতিসূচক ব্যবহার করিতেন। নবী করীম (স)-এর জীবদ্দশায় এক ব্যক্তি ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার কথা তাঁহার নিকট স্বীকার করে। তিনি সহানুভূতিশীল হইয়া তাহাকে তওবা করিতে ও এই অপরাধের কথা বলিয়া না বেড়াইতে উপদেশ দিলেন; কিন্তু অপরাধী শরীয়াতের নির্দিষ্ট দণ্ডবিধান হইতে আত্মরক্ষা করিতে প্রস্তুত না হওয়ায় নবী করীম (স)-এর দরবারে হাযির হইয়া নিজ ইচ্ছায় অপরাধ স্বীকার করিয়া এই দণ্ড গ্রহন করে।
খিলাফতের আমলেও হযরত আবূ বকর (রা)-এর এই প্রকৃতিই বর্তমান ছিল। নবুয়্যাতের মিথ্যা দাবিদার আশয়াস বিন কায়েস গ্রেফতার হইয়া তাঁহাদের দরবারে আসে। শেষ পর্যন্ত সে তওবা করিয়া প্রান ভিক্ষা চায়। হযরত আবূ বকর (রা) তাহাকে কেবল মুক্তিই দান করেন নাই, নিজের সহোদর ভগ্নীর সহিত তাহার বিবাহও সম্পন্ন করেন। বস্তুতঃরাজনৈতিক দৃষ্টিতে খলীফার প্রধান দায়িত্ব হইল জনগণের নৈতিক চরিত্র ও জান-মালের সংরক্ষন। এই দিক দিয়া যদিও তখন পর্যন্ত কোন পুলিশ বিভাগ স্থায়ীভাবে কায়েম ছিল না, তথাপি এই বিভাগটি তখনো নবী করীম (স)-এর স্থাপিত ব্যবস্থা অনুযায়ীই পরিচালিত হইতেছিল। অবশ্য হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা)কে পাহারাদারী ও নিরাপত্তা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিযুক্ত কড়া হইয়াছিল ও কয়েকটি বিশেষ বিশেষ অপরাধের দণ্ডও নির্ধারণ করা হইয়াছিল। এই ব্যাপারে তাঁহাকে ইসলামী পার্লামেন্টের মর্যাদাসম্পন্ন সাহাবা-সম্মেলনে কুরআন হাদীসের ভিত্তিতে পরামর্শ গ্রহন ও ইজতিহাদ করিতে হইয়াছে।
মোটকথা, জনজীবনের শান্তি ও নিরাপত্তা বিধান ও রাজপথসমূহকে সকল প্রকার বিপদ হতে মুক্ত ও নিরাপদ রাখার দিকে প্রথম খলীফা বিশেষ লক্ষ্য আরোপ করিতেন। এই কাজে কেহ বিন্দুমাত্র বাধা ও প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করিলেও তাহাকে কঠোর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিদান করিতেন। কিন্তু কোথাও শরীয়াতের দণ্ড-বিধানের সীমা কখনই লঙ্ঘন করিতেন না।
খিলাফতের অর্থ বিভাগ
নবী করীম (স)-এর যুগে অর্থ বিভাগ পরিচালনার জন্য কোন সুষ্ট ও সুসংগঠিত ব্যবস্থা ছিল না। বিভিন্ন সূত্র হইতে ধন-সম্পদ প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই তিনি উহা অভাবগ্রস্ত জনগণের মধ্যে বণ্টন করিতে দিতেন। হযরত আবূ বকর (রা) এর আমলে এই ব্যবস্থার কোন রদবদল করা হয় নাই। তিনি তাঁহার খিলাফতের প্রথম বৎসরেই মুক্ত ক্রীতদাস, স্ত্রী-পুরুষ এবং উচ্চ-নীচ সকল শ্রেণীর লোকদিগকে মাথাপিছু বিশ দিরহাম দান করিয়াছিলেন। ধন-বণ্টনের ব্যাপারে এইরূপ সমতা রক্ষা সম্পর্কে জনৈক সাহাবী আপত্তি পেশ করিলে তিনি জওয়াবে বলিয়াছিলেনঃ ‘লোকদের মর্যাদা ও গুন-গরিমার মধ্যে পার্থক্য অনস্বীকার্য; কিন্তু ধন-বণ্টনের ব্যাপারে কমবেশী হওয়ার সহিত উহার কি সম্পর্ক থাকিতে পারে?’ তাঁহার খিলাফতের শেষভাগে আনুষ্ঠানিকভাবে একটি ‘বায়তুলমাল’ প্রতিষ্ঠা করা হয়; কিন্তু উহাতে কখনো বিপুল পরিমাণ সম্পদ বা অর্থ সঞ্চিত হতে পারে নাই। ফলে বায়তুলমালের সংরক্ষণ ও পাহারাদারীর কোন ব্যবস্থা গ্রহণেরই প্রয়োজন দেখা দেয় নাই। একবার জনৈক সাহাবী এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেনঃ ‘উহার হেফাজতের জন্য একটি তালা-ই যথেষ্ট’। তাঁহার ইন্তেকালের পর হযরত উমর ফারুক (রা)-এর নেতৃত্বে ‘সানাই’ নামক স্থানে অবস্থিত বায়তুলমাল পরীক্ষা করিয়া দেখা হয় এবং উহাতে মাত্র একটি দিরহাম অবশিষ্ট রহিয়াছে বলিয়া প্রমানিত হয়। ইহা দেখিয়া জনগণ বলিয়া উঠিলঃ ‘আল্লাহ্ আবূ বকরকে রহম করুন’।
সামরিক ব্যবস্থা
নবী করীম (স) –এর আমলে কোন সুসংগঠিত ও সুশৃঙ্খল সৈন্যবাহিনী ছিল না। যুদ্ধের আওয়াজ শ্রুত হইলেই সমগ্র মুসলিম জনতা উহাতে যোগদানের জন্য প্রবল উৎসুক্যের সহিত নবী করীম (স)-এর সম্মুখে সমবেত হইতেন। হযরত আবূ বকর (রা)-এর আমলেও মোটামুটি এই প্রথাই চালু ছিল। অবশ্য তিনি একটি নূতন ব্যবস্থা চালু করিয়াছিলেন। তাহা এই যে, যখন কোন বাহিনী কোন বিশেষ অভিযানে প্রেরণ করিতেন, তখন সমগ্র সৈন্যদিগকে নান উপ-বাহিনীতে বিভক্ত করিয়া উহার প্রতিটির জন্য এক একজন সেনাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিয়া দিতেন। এইভাবে আমীরুল উমারা বা ‘কমান্ডার-ইন চীফ’ নিয়োগের প্রথাও প্রথম খলীফার আমলেই সূচিত হইয়াছিল এবং হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদই সর্বপ্রথম এই গুরুত্বপূর্ণ ও অত্যধিক সম্মানিত পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।
বস্তুতঃ সৈন্যবাহিনীকে এইভাবে সুসংবদ্ধ ও সন্নিবেশিত করার ফলে মুসলিম মুজাহিদীনের পক্ষে রোমকদের সুসংবদ্ধ সৈন্যবাহিনীর মুকাবিলা করা অতিশয় সহজ হইয়াছিল।
সৈনিকদের চরিত্রগঠন ও প্রশিক্ষন ব্যবস্থা
নবী করীম (স) ও খিলাফতে রাশেদার আমলে সংঘটিত প্রতিটি যুদ্ধ-সংগ্রাম আল্লাহ্র সন্তোষ বিধান ও ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষার উদ্দেশ্যই চালিত হইয়াছে। এই কারণে এই উদ্দেশ্য আত্মোৎসর্গীকৃত জনতার নৈতিক চরিত্রের উন্নতি বিধানের দিকে তখন বিশেষ গুরুত্ত সহকারে দৃষ্টি দেওয়া হইত। ফলে ইসলামী বাহিনী নৈতিক চরিত্রের দিক দিয়া সমগ্র বিশ্বের শ্রেষ্টত্তের অধিকারী হইয়াছিল। নবী করীম (স)-এর পরে হযরত আবূ বকর (রা) ও সামরিক প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে এই দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াছেন। বিশেষ বিশেষ অভিযানে সৈন্যবাহিনী প্রেরণের সময় তিনি সেনাধ্যক্ষর সহিত বহুদূর অগ্রসর হইয়া যাইতেন ও মূল্যবান উপদেশ দান করিয়া তাহাকে বিদায় দিতেন। সিরিয়া অভিযানে প্রেরণের সময় সেনাধ্যক্ষর নিম্নোক্তরুপে উপদেশ দিয়াছিলেনঃ
তোমার এমন লোকদের সাক্ষাত পাইবে, যাহারা আল্লাহ্র উপাসনায় আত্মনিয়োগ করিয়া রহিয়াছেন। তাহাদের উপর আক্রমন করিবে না। এতদ্ব্যতীত আরও দশটি উপদেশ তোমাদিগকে দিতেছিঃ কোন স্ত্রী, শিশু ও বৃদ্ধ লোককে হত্যা করিবে না, ফলবান গাছ কর্তন করিবে না, কোন জনপদ বা আবাদ স্থানকে জনশূন্য করিবে না। ছাগল ও উষ্ট্র খাদ্য-প্রয়োজন ব্যতীত কখনো জবেহ করিবে না। খেজুর বাগানে অগ্নিসংযোগ করিবে না। গণিমতের মাল কোনরূপ অপহরণ করিবে না এবং কাপুরুষ ও সাহসহীন হইবে না।
যুদ্ধের সরঞ্জাম সংগ্রহ
হযরত আবূ বকর (রা) যুদ্ধের সরঞ্জাম সংগ্রহের জন্য একটি নির্দিষ্ট পরিকল্পনা কার্যকর করিয়াছিলেন। বিভিন্ন সূত্রে সরকারী ফান্ডে যাহা কিছু জমা হইত, উহা হইতে একটি মূল্যবান অংশ তিনি পরিবহন ও অস্ত্র ক্রয়ের কাজে ব্যয় করিতেন। কুরআন মজীদে গণিমতের মালে আল্লাহ্, রাসূল ও নিকটাত্মীয়দের জন্য যে অংশ নির্দিষ্ট করা হইয়াছে, তাহা সবই এই সামরিক প্রয়োজন পূরণের খাতে ব্যয় করা হইত। নবী করীম (স) অন্যান্য জরুরী কাজের পর এই খাতেই অবশিষ্ট সম্পদ ব্যয় করিতেন।
উষ্ট্র ও অশ্ব পালনের প্রথম খলীফা ‘বকী’ নামক স্থানে একটি বিশেষ চারণভূমি নির্দিষ্ট করিয়াছিলেন। এখানে হাজার হাজার সরকারী জন্তু প্রতিপালনের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। সদকা ও যাকাত বাবদ আদায়কৃত সরকারী জন্তু এখানেই রাখা হইত।
সামরিক কেন্দ্রসমূহ পর্যবেক্ষণ
হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) বার্ধক্যজনিত দুর্বলতার ফলে নানা দুশ্চিন্তা ও মনোবেদনায় ভারাক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও নিজেই সামরিক ছাউনীসমূহ পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ করিতেন এবং সৈনিকদের মধ্যে বাস্তব ও আধ্যাত্মিকতার দিক দিয়া কোন ত্রুটি –বিচ্যুতি দেখিতে পাইলে সঙ্গে সঙ্গে উহার সংশোধনও করিয়া দিতেন। কোন একটি বিশেষ অভিযান উপলক্ষে ‘জরফ’ নামক স্থানে বিপুল সংখ্যক সৈন্য সমাবেশ করা হয়। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) উহা পরিদর্শন করিতে গেলেন। তিনি ‘বানুফজারাহ’ নামক স্থানে অবস্থিত তাঁবুতে উপস্থিত হইতে মুজাহিদগণ দাঁড়াইয়া তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিল। এখানে তিনি বিভিন্ন গোত্র হইতে আগত সৈনিকদের মধ্যে পারস্পরিক আভিজাত্য ও শ্রেষ্টত্তের গৌরববোধ লক্ষ্য করিলেন। তিনি উপদেশের সাহায্যে বংশীয় ও গোত্রীয় আভিজাত্য এবং পারস্পরিক হিংসা-দ্বেষ অবদমিত করিয়া সকলের মধ্যে ইসলামী সহনশীলতা ও ভ্রাতৃত্ববোধ জাগাইবার জন্য চেষ্টা করিলেন।
অনৈসলামী প্রথার প্রতিরোধ
নবীদের প্রচারিত ধর্মমত ও জীবন ব্যবস্থার উত্তরকালে বিকৃত হইয়া যাওয়ার মূলে সবচেয়ে বড় কারণ হইল লোকদের মধ্যে ক্রমশঃ বিদয়াতের প্রচলন ও প্রশ্রয় লাভ। ইহার ফলে, বিদয়াতী ব্যবস্থাসমূহই মূল ধর্মের স্থান লাভ করে ও আসল ধর্ম বিলুপ্ত হয়। হযরত আবূ বকর (রা)-এর আমলে ইসলামী সমাজে বিদয়াতের কোন বিশেষ সূচনা পরিলক্ষিত হয় নাই। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও কখনও এবং কোথাও তেমন কিছু দেখা গেলেই তিনি অনতিবিলম্বে উহা দূর করিতে চেষ্টিত হইতেন।
কুরআন ও হাদীস সম্পর্কে হযরত আবূ বকর (রা)-এর ভূমিকা
নবুয়্যাতের মিথ্যা দাবিদারদের সহিত সংঘটিত লড়াইসমূহে বহুসংখ্যক হাফিজে কুরআন মুজাহিদ শহীদ হন। বিশেষতঃইয়ামামার রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে এত বেশিসংখ্যক হাফিজে কুরআন শাহাদত বরণ করেন যে, তাহাতে দায়িত্তসম্পন্ন সাহাবীদের মনে কুরআন মজীদের বিলুপ্ত হইয়া যাওয়ার আশংকা দেখা দেয়। এই জন্য অবিলম্বে কুরআন মজীদ সংগ্রহ, প্রণয়ন ও সন্নিবেশিত করার প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে দেখা দেয়।
বস্তুতঃকুরআন মজীদের আয়াত ও সূরাসমূহ বিশেষ বিশেষ সময়ে ও বিশেষ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নাজিল হইয়াছে এবং নবী করীম (স)-এর নির্দেশে তাহা সঙ্গে সঙ্গেই নির্দিষ্ট সাহাবীদের দ্বারা লিখিত হইয়াছে। খর্জুর পত্র, উষ্ট্রের চামড়া, অস্থি, পাথর ও কাষ্ঠের উপরই তাহা সুস্পষ্টরুপে লিখিত ছিল। হযরত আবূ বকর (রা)-এর নির্দেশে তাহা একত্রে সন্নিবেশিত করা হয় ও একখানা সুসংবদ্ধ গ্রন্থের রূপ দান করা হয়। ইসলামী দৃষ্টিতে ইহা যে কত বড় কীর্তি ছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়।
হাদীস সম্পর্কে হযরত আবূ বকর (রা)-এর ভূমিকা ছিল অত্যন্ত সতর্কতাপূর্ণ। তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন যে, কোন হাদীসের সত্যতা সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাসী ও সর্ব প্রকারের সন্দেহ বিমুক্ত না হইয়া উহা রেওয়ায়েত করা ঠিক নহে। তিন নিজে কখনো কোন হাদীসকে উহার একাধিক সমর্থক ও সাক্ষী না পাইলে গ্রহন করিতেন না।
ইসলামী আইন বিভাগ স্থাপন
ইসলামী আইন সম্পর্কে গবেষণা, অনুসন্ধান ও বিচার-বিশ্লেষণের গুরুত্বপূর্ণ কার্য সম্পাদনের জন্য হযরত আবূ বকর (রা) একটি বিশেষ বিভাগ স্থাপন করেন। হযরত উমর, হযরত উসমান, হযরত আলী, হযরত আবদুর রাহমান বিন আউফ, হযরত মুয়াজ বিন জাবাল, হযরত উবাই বিন কায়াব, হযরত জায়েদ বিন সাবেত (রা) প্রমুখ শ্রেষ্ঠ মনিষী ও চিন্তাবিদগণ এই কাজে নিযুক্ত ছিলেন। জনগণের জিজ্ঞাসিত ফতোয়ার জওয়াব দান করাও ইঁহাদেরই দায়িত্ব ছিল।
ইসলাম প্রচার
রাসূলের প্রতিনিধি মর্যাদাসম্পন্ন খলীফার অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ছিল ইসলামী আদর্শ প্রচার। এই দিকে হযরত আবূ বকর (রা)-এর প্রথম হইতেই বিশেষ লক্ষ্য ও দৃষ্টি ছিল। বস্তুতঃইসলামী আকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্রসমূহ ছিল সত্যের জন্য আত্মোৎসর্গীকৃতপ্রাণ হযরত আবূ বকর (রা)-এর আপ্রান প্রচেষ্টার ফসল। কিন্তু খিলাফতের গুরুভার অর্পিত হওয়ার পর স্বাভাবিকভাবেই এইদিকে তাঁহার অধিক প্রবণতা ও তৎপরতা দেখা দেয়। ফলে সমস্ত আরবদেশ ইসলাম প্রচারের বলিষ্ঠ ধ্বনিতে মুখরিত হইয়া উঠে। চতুর্দিকে প্রেরিত মুজাহিদদিগকে ইসলাম প্রচারের জন্য হযরত আবূ বকর (রা) নির্দেশ দিলেন। বিভিন্ন অঞ্চলে বিক্ষিপ্ত আরব গোত্রসমূহে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছাইবার জন্য তিনি বিশেষ প্রতিনিধি দল প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা পূর্ণ একাগ্রতা ও ঐকান্তিক নিষ্ঠা সহকারে এই কাজ সম্পন্ন করিতেন। ইহার ফলে দূর-নিকটের সকল মূর্তিপূজক ও খৃষ্টান ধর্মাবলম্বী ইসলামে দীক্ষিত হয়। হযরত খালেদ (রা)-এর ইসলামী দাওয়াতে সাড়া দেয় ইরাক, আরব ও সিরীয় সীমান্তবর্তী আরব গোত্রসমূহ।
নবী করীম (স)-এর ওয়াদাসমূহ পরিপূরণ
নবী করীম (স)-এর আমলের ঋণসমূহ পরিশোধ করা ও প্রদত্ত ওয়াদা-প্রতিশ্রুতিসমূহ যথাযথভাবে পালন করাও খিলাফতের অন্যতম দায়িত্ব ছিল। হযরত আবূ বকর (রা) প্রথম অবসরেই এ কাজগুলি সম্পন্ন করেন। বিশেষতঃ ‘বাহরাইন’ বিজয়ের ফলে বিপুল ধনসম্পদ হস্তগত হইলে পর তিনি সাধারণভাবে ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, নবী করীম (স)-এর নিকট কাহারো পাওনা থাকিলে কিংবা তাঁহার কোন ওয়াদা অপূর্ণ থাকিলে আমার নিকট হইতে তাহা পূরণ করা যাইতে পারে।
নবী করীম (স)-এর পরিবারবর্গ ও আত্মীয়দের সহিত ব্যবহার
নবী করীম (স)-এর পরিবারবর্গ ও নিকটাত্মীয়দের সহিত ‘ফিদাকের’ বাগানকে কেন্দ্র করিয়া প্রথমে তাঁহার সহিত কিছুটা ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হইলেও তিনি তাঁহাদের সহিত সকল সময় অত্যন্ত হৃদ্যতা,সহানুভূতি, ও শ্রদ্ধাপূর্ণ ব্যবহার করিয়াছেন। উম্মাহাতুল মু’মিনীনের সুখ-শান্তি বিধান ও তাঁহাদের যাবতীয় প্রয়োজন পূরণের দিকে তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য লোকদের সম্পর্কে রাসূলে করীম (স) যেসব অসীয়ত করিয়া গিয়াছেন, তিনি পূর্ণ সম্মান ও ভক্তিসহকারে সেইগুলি পূরণ করিয়াছেন।
যিম্মি প্রজাদের অধিকার রক্ষা
নবুয়্যাতের যুগে ইসলাম রাষ্ট্রে যে সব বিধর্মীদের আশ্রয়দান করা এবং লিখিত চুক্তিনামার মাধ্যমে যাহাদের সহিত বিশেষ সন্ধি করা হইয়াছিল, হযরত আবূ বকর (রা) তাহাদের যাবতীয় অধিকার যথাযথরূপে রক্ষা করিয়াছেন। অনুরুপভাবে তাঁহার খিলাফত আমলে বিজিত দেশসমূহে অমুসলিম যিম্মী প্রজাদের তিনি মুসলিম প্রজাদের প্রায় সমান অধিকার দান করিয়াছিলেন। ‘হীরা’র খৃষ্টান অধিবাসীদের সহিত যে চুক্তি-নামা স্বাক্ষরিত হইয়াছিল, তাহা নিম্নরুপঃ
তাহাদের খানকাহ ও গীর্জাসমূহ ধ্বংস করা হইবে না, প্রয়োজনের সময়ে আশ্রয় গ্রহণের উদ্দেশ্যে নির্মিত কোন প্রাসাদও চূর্ণ করা হইবে না। ঘণ্টা বাজানো ও শিঙ্গা ফুকাইতে বাধা দেওয়া হইবে না। তাহাদের বিশেষ উৎসব অনুষ্ঠানের সময়ে ক্রুশ মিছিল বাহির করিতে নিষেধ করা হইবে না।
দীর্ঘ চুক্তিনামা হইতে এখানে মাত্র কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করা হইল। ইহা হইতে ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় পরধর্ম-সহিষ্ণুতার উজ্জ্বল নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়।
প্রথম খলীফার আমলে জিজিয়া ও সাধারণ করের পরিমাণ ছিল অত্যন্ত কম। উপরন্তু তাহা কেবল সামর্থ্যবান লোকদের উপর ধার্য করা হইত। ‘হীরা’ অঞ্চলের সাত সহস্র অধিবাসীর মধ্যে এক সহস্র অধিবাসীকেই সকল প্রকার জিজিয়া কর হইতে নিষ্কৃতি দেওয়া হইয়াছিল আর অবশিষ্ট লোকদের উপরও মাথাপিছু বার্ষিক মাত্র দশ দিরহাম কর ধার্য করা হইয়াছিল। উল্লেখিত চুক্তিতে ইহারও উল্লেখ ছিল যে, কোন যিম্মী বৃদ্ধ, অক্ষম ও দরিদ্র হইয়া গেলে তাহার নিকট হইতে কোন করই গ্রহন করা হইবে না; উপরন্তু বায়তুলমাল হইতে তাহার ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করা হইবে। দুনিয়ার ইতিহাসে এইরূপ অপক্ষপাত প্রজাপালন ও উদার আচরণের কোন দৃষ্টান্ত খুঁজিয়া পাওয়া যায় কি?
উমর ফারুক (রা)-এর চরিত্র বৈশিষ্ট্য
বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (স) স্বীয় জীবনের অকৃত্রিম সাধনার ফলে এক পূর্ণাঙ্গ আদর্শবাদী ও উন্নত চরিত্রবিশিষ্ট সমাজ গঠন করিয়াছিলেন। তাঁহার গঠিত সমাজের প্রতিটি ব্যক্তিই আদর্শবাদী ও নৈতিক চরিত্রের দিক দিয়া ছিল পর্বত-শৃংগের মত উন্নত, অন্যায় ও বাতিলের সম্মুখে অনমনীয় এবং বিরুদ্ধবাদীদের দৃষ্টিতে অত্যন্ত দুর্জয় ও দুর্ভেদ্য। প্রায় সকল সাহাবী সম্পর্কেই এই কথা পূর্ণ মাত্রায় সত্য ও প্রযোজ্য। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ইহা অনস্বীকার্য যে কোমলতা, কঠোরতা, বিনয়,নম্রতা এবং সহিষ্ণুতার দিক দিয়া তাঁহাদের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান ছিল। এই পার্থক্য স্বভাবগত তারতম্যের কারণে এক বাস্তব সত্যরূপে স্বীকৃত। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা যখন হযরত উমর ফারুক (রা)-এর ব্যক্তি চরিত্র পর্যালোচনা করি, তখন আমাদের সম্মুখে এক অসাধারণ লৌহ-মানবের বিস্ময়কর ভাবমূর্তি সমুদ্ভাসিত হইয়া উঠে। বস্তুত হযরত উমর (রা) ইসলামী সমাজে এক অপরিসীম বীর্যবান, তেজোময়, নির্ভীক ও অনমনীয় ব্যক্তিত্তের অত্যুজ্জ্বল আদর্শ সংস্থাপন করিয়াছেন। ইসলামী খিলাফতের বিশাল আকাশে তিনি এক দেদীপ্যমান চন্দ্রের সমতুল্য। খিলাফতের ময়দানে তাঁহার ভূমিকা অত্যন্ত বলিষ্ঠ ও সমুন্নত।
উমর চরিত্রের এই বলিষ্ঠতা তাঁহার জীবনের প্রথমকাল হইতেই পরিলক্ষিত হয়। ইসলাম-পূর্ব যুগের সমাজে তিনি এক অসামান্য বীর-পুরুষ রুপেই পরিচিত ছিলেন। তিনি যখন সাতাইশ বৎসরের এক উদীয়মান বীর যুবক, ঠিক তখনি আরবের মরুবক্ষে ইসলাম-সূর্যের অভ্যুদয় ঘটে। মক্কার পর্বতচূড়া হইতে দিক প্রকম্পক তওহীদ বানী ধ্বনিত হয়। উমর ফারুকের নিকট এই ধ্বনি ছিল সম্পূর্ণ অভিনব ও অপরিচিত। তিনি ইহা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ও বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠেন। ফলে যাহার সম্পর্কেই তিনি ইসলাম কবুল করার খবর পাইতেন, তিনি তাহারই প্রচণ্ড শত্রু হইয়া দাঁড়াইতেন। তাঁহার বংশেরই একটি ক্রীতদাসী ইসলাম কবুল করিলে তাহাকে তিনি অবিশ্বাস্য রকমে প্রহার করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত আর যাহার সম্পর্কেই তিনি ইসলাম কবুল করার সংবাদ পাইতেন, তাঁহাকেই তিনি নাস্তানাবুদ করার জন্য দৃপ্ত পদক্ষেপে অগ্রসর হইতেন। কিন্তু বড়ই আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, এত আঘাত করিয়াও তিনি একটি মাত্র লোককেও ইসলাম ত্যাগে প্রস্তুত করিতে পারনে নাই। শেষ পর্যন্ত তিনি স্বয়ং বিশ্বনবীকেই খতম করার সিদ্ধান্ত গ্রহন করেন। একদা তীক্ষ্ণ শানিত কৃপাণ স্কন্ধে ঝুলাইয়া দৃপ্ত পদক্ষেপে তিনি সেই উদ্দেশ্যেই যাত্রা করিলেন। কিন্তু পথিমধ্যে যখনি তিনি শুনিতে পাইলেন যে, তাঁহারই আপন ভগ্নি ও ভগ্নিপতি ইসলাম কবুল করিয়াছেন, তখন তাঁহার উপর যেন বজ্রপাত হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া গিয়া ভগ্নী ও ভগ্নীপতিকে এতই প্রহার করেন যে, তাঁহাদের দেহ হইতে রক্তের অবরল ধারা প্রবাহিত হইতে শুরু করে। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও তাঁহাদের দিলে ইসলামের প্রতি ঈমানের একবিন্দু দুর্বলতা দেখা দেয় নাই। উপরন্তু তাঁহারা উমর ফারুককে সম্বোধন করিয়া বলিলেনঃ “তোমার মনে যাহা আসে কর। কিন্তু আমাদের দিল হইতে ইসলামের প্রতি ঈমানের অত্যুজ্জ্বল দীপমশাল নির্বাপিত করা তোমার সাধ্যাতীত”।
নওমুসলিমদের এই অনমনীয়তা দর্শনে উমর ফারুক (রা) বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়েন। কি কারণে ইহারা ইসলামের জন্য এতদূর আত্মহারা ও উৎসর্গীকৃতপ্রাণ হয় এবং কোন পরশপাথরের ছোঁয়ায় একজন অসভ্য নাফরমান লোক মানুষ পদবাচ্য হইয়া উঠে তাহা ভাবিয়া তিনি দিশাহারা হইয়া যান। শেষ পর্যন্ত তিনিও ইসলামের সুদৃঢ় নীতি-দর্শনের সম্মুখে মস্তক অবনত করিতে বাধ্য হন। তাঁহার ন্যায় একজন অসামান্য বীর-পুরুষের ইসলাম গ্রহণে তদানীন্তন আরবের দুই পরস্পর বিরোধ সমাজেই দারুণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। কাফির সমাজ যেমন আশ্চার্যািন্বত হয় তেমনি হয় হতাশাগ্রস্ত; পক্ষান্তরে ক্ষুদ্র পরিসরের ইসলামী সমাজে উৎসাহ উদ্দীপনার এক যৌবন জোয়ার পরিলক্ষিত হয়, তখন মুসলমানরা ছিলেন অতিশয় দুর্বল, শক্তিহীন ও অসহায়। প্রকাশ্যভাবে ইসলামী জিন্দেগী যাপন ও জরুরী অনুষ্ঠানাদি পালন তো দূরের কথা, নিজদিগকে মুসলিমরূপে ব্যক্ত করাও তাঁহাদের পক্ষে কঠিন বিপদের কারণ হইয়া পড়িয়াছিল। বিশেষতঃতাহাদের পক্ষে আল্লাহ্র ঘরে আল্লাহ্র বন্দেগী করা তো ছিল একেবারে অসম্ভব। হযরত উমর (রা)-এর ন্যায় নির্ভীক বীর পুরুষের ইসলাম গ্রহণে সহসা অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। তিনি নিজেই মুসলিম হওয়ার কথা রাষ্ট্র করিয়া দিলে কাফির সমাজ তাঁহার প্রতি অত্যন্ত বিরুপ ও ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে। তাঁহার মামা প্রভাবশালী কাফির নেতা আস বিন ওয়ায়েল তাঁহাকে আশ্রয় দিতে চাহিলে তিনি তাঁহার স্বভাবসুলভ তেজস্বীতা ও বীর্যবত্তার দরুণ তাহার আশ্রয় গ্রহন করিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। কেননা ইসলামের বিপ্লবী কালেমা ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু’র উপর বিশ্বাস স্থাপনের পর কোন কাফির ব্যক্তি বা শক্তির আশ্রয় গ্রহন করা, কোন আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে মোটেই শোভন ব্যাপার নহে। উপরন্তু তিনি মুসলিমদের সমভিব্যহারে কা’বা ঘরে গিয়াই নামায আদায় করেন। মূলত বীর উমরের সাহসিকতার বলেই এই কাজটি সম্ভব হইয়াছিল। এইজন্য নবুয়্যাতের দরবারে তিনি ফারুক (হক ও বাতিলের পার্থক্যকারী) উপাধিতে ভূষিত হন।
হযরত উমর (রা) ইসলাম গ্রহণের পর হিজরাত পর্যন্ত মক্কা শরীফে প্রায় ছয়-সাত বৎসরকাল অবস্থান করেন। এই সময় কাফিরদের তরফ হইতে মুসলিমদের উপর যে অমানুষিক অত্যাচার ও জুলুম-নিষ্পেষণ সংগঠিত হয়, অন্যান্যদের সঙ্গে হযরত উমর (রা) ও তাহা অবলীলাক্রমে সহ্য করিয়াছেন। বস্তুত ইসলামের জন্য অতুলনীয় আত্মোৎসর্গিতা,অপূর্ব নৈতিক দৃঢ়তা ও চারিত্রিক অনমনীয়তা না থাকিলে কাফিরদের পৈশাচিক নির্যাতনের যাতাকলে নিষ্পিষ্ট হইয়াও ঈমানকে বাঁচাইয়া রাখা তদানীন্তন মুসলিমদের পক্ষে বড়ই কঠিন ব্যাপার ছিল।
ইসলামের প্রথম যুদ্ধ বদরের ময়দানে সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে হযরত উমর (রা)যে সূক্ষ্ম বিচার-বুদ্ধি,আত্মোৎসর্গী ভাবধারা ও অনমনীয় দৃঢ়তা প্রদর্শন করেন, ইসলামের ইতিহাসে তাহা উজ্জ্বল অক্ষরে লিখিত। ইসলামের জন্য তিনি অতি বড় নিকটাত্মীয়কেও একবিন্দু ক্ষমা করিতে প্রস্তুত হন নাই। যুদ্ধের ময়দানে তাঁহার মামা ‘আস তাঁহার নিজ তরবারীর আঘাতেই নিহত হয়। এই পরম আত্মীয়ের বক্ষে অস্ত্র বিদ্ধ করিতেও তিনি কিছু মাত্র কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। ইসলামের জন্য এই আত্মত্যাগ বস্তুতঃই তুলনাহীন।
বদর যুদ্ধে মুসলিমরা গৌরবোজ্জ্বল বিজয় অর্জন করে এবং ইহাতে কম-বেশী সত্তর জন কাফির সরদার মুসলিমদের হস্তে বন্দি হয়। ইহাদের সহিত কিরুপ ব্যবহার করা হইবে, তাহা লইয়া আলোচনা শুরু হইলে হযরত উমর ফারুক (রা) স্পষ্ট অভিমত প্রকাশ করিয়া বলিলেনঃ “ইহাদের হত্যা করাই বাঞ্ছনীয় এবং আমাদের মধ্যে প্রত্যেকেরই নিজ নিজ আত্মীয়কে নিজ হস্তে যবেহ করা কর্তব্য”।
ষষ্ট হিজরী সনে চৌদ্দ শত মুসলিম সমভিব্যাহারে নবী করীম (স) হজ্জের উদ্দেশ্যে মক্কা যাত্রা করেন। যুলহুলায়ফা নামক স্থানে পৌঁছিয়া তিনি জানিতে পারেন যে, মক্কার কুরাইশগন এই বৎসর মুসলিমদিগকে কিছুতেই নগরীতে প্রবেশ করিতে দিবে না। এই পরিস্থিতিতে হযরত উসমান (রা) কে শহীদ করিয়া ফেলার সংবাদ ছড়াইয়া পড়ে। এই সময় নবী করীম (স) সাহাবীদের নিকট হইতে আত্মোৎসর্গের ‘বায়’আত’ গ্রহন করেন। হযরত উমর (রা) ইহাতে অগ্রবর্তী ছিলেন। শেষ পর্যন্ত কুরাইশদের সহিত সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরিত হইলে উহার একটি শর্ত উমর ফারুক (রা)-এর নিকট সুস্পষ্টরূপে অগ্রহণযোগ্য মনে হয় এবং তাঁহার প্রখর আত্মসম্মানবোধ সাহসিক প্রকৃতিতে প্রচণ্ড আঘাত হানে। তিনি অনতি-বিলম্বে রাসূলের দরবারে উপস্থিত হইয়া আরজ করিলেনঃ “আমরা যখন বাস্তবিকই সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, তখন বাতিলের সহিত এত নম্র ও নত হইয়া সন্ধি করার প্রয়োজন কি?”
মক্কা বিজয়ের বৎসরই হুনাইন যুদ্ধ সংঘটিত হয়। হযরত উমর (রা) এই যুদ্ধে অত্যন্ত দৃঢ়তা সহকারে লড়াই করেন। নবম হিজরীতে যখন রোমান সম্রাটের মদীনা আক্রমণের সংবাদ ছড়াইয়া পড়ে, তখন নবী করীম (স)-এর আবেদনক্রমে হযরত উমর ফারুক (রা) তাঁহার মোট সম্পত্তির অর্ধেক আনিয়া রাসূলের খেদমতে পেশ করেন।
বিশ্বনবীর ইন্তেকালের সংবাদ পাইয়া গোটা মুসলিম সমাজ প্রচণ্ড মর্ম জ্বালায় ভাঙ্গিয়া পড়ার উপক্রম হয়। এদিকে কুটিল চরিত্রের মুনাফিকগন সুযোগ বুঝিয়া কোন মারাত্মক বিপর্যয় সৃষ্টির জন্য চেষ্টিত হইতে পারে মনে করিয়া হযরত উমর ফারুক (রা) মসজিদে নববীতে দাঁড়াইয়া ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা করিতে শুরু করেনঃ “যে বলিবে বিশনবী ইন্তেকাল করিয়াছেন, তাঁহার গর্দান উড়াইয়া দেওয়া হইবে”। বস্তুত ইহা ছিল হযরত উমর (রা)-এর সহজাত তেজোবীর্যেরই বাস্তব অভিব্যাক্তি মাত্র।
হযরত উমর (রা)-এর চরিত্রে যে তেজস্বিনী ও অনমনীয় ভাবধারা পূর্বাপর পরিলক্ষিত হয় কোন কোন সাহাবার উপর ইহার কিছুটা বিরুপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) যখন জীবনের শেষ পর্যায়ে উপনীত হইয়া পরবর্তী খলীফা নিয়োগের চিন্তায় অধীর হইয়া পড়েন, তখন তিনি ব্যক্তিগতভাবে হযরত উমর (রা)কে এই পদে অভিষিক্ত করার পক্ষে মত ব্যক্ত করেন। তিনি তাঁহার জীবনের দীর্ঘ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে নিঃসন্দেহে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন যে, তাঁহার অন্তর্ধানের পর উমর ফারুক (রা)-ই হইতেছেন খিলাফতের জন্য সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত ব্যক্তি। তিনি হযরত আবদুর রহমান বিন আউফ (রা)-এর নিকট যখন তাহার এই মত প্রকাশ করিলেন, তখন তিনি বলিলেনঃ ‘উমর ফারুক সম্পর্কে আপনার যে মত, আল্লাহ্র শপথ তিনি তাহা হইতেও উত্তম। কিন্তু চিন্তার বিষয় এই যে, তাঁহার প্রকৃতিতে তীব্রতা ও কঠোরতা অত্যন্ত বেশী’।(তাবারী) ইহার উত্তরে হযরত আবূ বকর (রা) বলিলেনঃ “ইহার কারণ এই যে, আমার মধ্যে ছিল অত্যধিক নম্রতা ও বিনয়। কিন্তু তাঁহার নিজের উপরই যখন দায়িত্ব অর্পিত হইবে, তখন তিনি তাঁহার অনেক অভ্যাস ও স্বভাবই পরিত্যাগ করিবেন। হে আবূ মুহাম্মাদ! আমার অভিজ্ঞতা এই যে, আমি কাহারো প্রতি ক্রুদ্ধ হইলে আমার ক্রোধাগ্নি নির্বাপিত করার জন্য উমরই চেষ্টিত হইতেন ও আমাকে নম্র ভাব অবলম্বনের পরামর্শ দিতেন’। (আল-ইসলাম অল-হিযারাতুল আরাবিয়া)।
হযরত উমর ফারুক (রা)-এর কঠোর প্রকৃতি সম্পর্কে হযরত আবূ বকর (রা)-কে জনগণের নিকটও জওয়াবদিহি করিতে হইয়াছে। তাঁহার পরবর্তী খলীফা সম্পর্কে তাঁহার মত যখন জনগণের মধ্যে প্রচারিত হইয়া পড়ে, তখন কিছু সংখ্যক লোক আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেঃ “উমরের মত কঠোর প্রকৃতির ব্যক্তিকে স্বীয় স্থলাভিষিক্ত করিলে আল্লাহ্র নিকট পৌঁছিয়া আপনি কি জবাব দিবেন?” হযরত আবূ বকর (রা) তাহাদের ভুল মতের অত্যন্ত সূক্ষ্ম পন্থায় প্রতিবাদ করিয়া বলিলেনঃ “আমি আল্লাহ্র সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিব যে, পরবর্তী উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম ব্যক্তিকেই আমি খলীফা হিসাবে পছন্দ করিয়াছি”।
বস্তুতঃনবী করীম (স)-এর দরবারে হযরত আবূ বকর (রা)-এর যে মর্যাদা ছিল, হযরত আবূ বকর (রা)-এর দরবারে অনুরূপ মর্যাদা ছিল হযরত উমর ফারুক (রা)-এর। (মুকদ্দমা ইবনে খালদুন ২০৬ পৃঃ) এইজন্য হযরত আবূ বকর (রা)-এর উপরোল্লিখিত উক্তি সম্পূর্ণ সত্য।
হযরত উমর (রা) খলীফা পদে অভিষিক্ত হওয়ার পর সর্বপ্রথম যে বাণী তাঁহার কণ্ঠনিঃসৃত হইয়া মুসলিম জনগণের কর্ণকুহরে প্রবেশ করে তাহা এইঃ ‘আরবগণ, রশি-বাঁধা উষ্ট্রের ন্যায় চালকের পশ্চাতে পশ্চাতে চলাই তোমাদের ধর্ম। কিন্তু চালক কোথায় কিভাবে লইয়া যায়, তাহাই লক্ষণীয়। তবে আমার সম্পর্কে বলিতে পারি-কা’বা ঘরের আল্লাহ্র কসম, আমি তোমাদিগকে অবশ্যই সঠিক পথে আনিয়া ছাড়িব’।
হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর দাফন কার্য সমাপ্ত হওয়ার অব্যবহিত পরই তিনি নিজ হস্ত হইতে মৃত্তিকা ঝাড়িয়া ফেলিয়া ভাষণ দানের জন্য দণ্ডায়মান হইলেন। সমবেত ইসলামী জনতাকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিলেনঃ
মুসলিম জনতা! আল্লাহ্ তোমাদিগকে ও আমাকে এক সাথে শামিল করিয়া দিয়াছেন। আর আমার প্রাক্তন দুই সঙ্গীর পর আমাকে জিন্দাহ ও অবশিষ্ট রাখিয়াছেন। আল্লাহ্ শপথ, আমার সম্মুখে যে সকল ব্যাপার উপস্থাপিত হইবে, তাহা সবই আমি মীমাংসা করিব। আর যাহা কিছু আমার অগোচরে থাকিয়া যাইবে, সেই বিষয়ে আমি পূর্ণ দায়িত্বজ্ঞান ও আল্লাহপরস্তি সহকারে চেষ্টা করিব। বস্তুতঃলোকেরা যদি আমার প্রতি ইহসান ও কল্যাণের আচরণ গ্রহন করে, আমিও তাহাদের সহিত অনুরূপ ব্যবহারই করিব। কিন্তু যদি কেহ খারাপ ও অবাঞ্ছনীয় আচরণ অবলম্বন করে, তাহা হইলে আমিও তাহাকে কঠোর শাস্তি দান করিব’।
হযরত উমর (রা)-এর এই নীতি-নির্ধারণী ভাষণই ছিল তাঁহার খিলাফতের কার্যসম্পাদনের দিক-নির্দেশিকা। অভিজ্ঞ লোকদের সুস্পষ্ট অভিমত এই যে, তিনি আগা-গোড়া তাঁহার এই কথা অনুযায়ীই কাজ করিয়াছেন। ইহার এক বিন্দু কমও করেন নাই, বেশীও করেন নাই।
হযরত উমর (রা) নিজেই আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করিতেনঃ
********(আরবী)
হে আল্লাহ্, আমি স্বভাবতই কঠোর প্রকৃতির লোক, আমাকে নম্র ও আর্দ্র করিয়া দাও। আমি দুর্বল, আমাকে শক্তি দান কর। আমি কৃপণ, আমাকে দানশীল বানাইয়া দাও। (আল ইসলাম অল-হিযারাতুল আরাবিয়া)
হযরত উমর (রা) খলীফা নিযুক্ত হওয়ার পর ইরাক অভিযানকে শক্তিশালী করার জন্য তিনি বিপুল সংখ্যক সৈন্য প্রেরণে উদ্যোগী হন। এই উদ্দেশ্য প্রকাশ্য জনসভায় উপর্যুপরি কয়েকদিন পর্যন্ত আবেদন করার পরও তিনি এক মর্মস্পর্শী ও উদ্দীপনাময় ভাষণ দান করে। উহার ফলে মুসলিম জনতা দলে দলে জিহাদে যোগদানের জন্য প্রস্তুত হয়। এই অব্যাহত সংগ্রামধারার শেষ পর্যায়ে ইরানের সঙ্গে মুসলমানদের প্রকাশ্য সংঘর্ষ ঘটে। কিন্তু মুসলিমগণ ইহাতে পরাজিত হন ও নয় সহস্র সৈনিকের মধ্যে মাত্র তিন সহস্র অবশিষ্ট থাকে। এই পরাজয়ের সংবাদ পাইয়া হযরত উমর ফারুক বেজায় অসন্তুষ্ট ও ক্রুদ্ধ হন। তখন তিনি ইসলামের জন্য আত্মদানের আহবান জানাইয়া যে জ্বালাময়ী বক্তৃতা করেন, আরব গোত্রসমূহের মধ্যে তাহা অগ্নুৎগীরণের সৃষ্টি করে। এমন কি অসংখ্য খৃস্টান নাগরিকও এই যুদ্ধে মুসলিমদের সহিত সংগ্রাম ক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়িতে প্রস্তুত হয়।
হযরত উমর ফারুক (রা)-এর খিলাফতকালে ইসলামের অপূর্ব বিজয় সাধিত হয়। মিশর, সিরিয়া, ইরাক, আর্মেনিয়া, ইরান, ফিলিস্তিন, আজারবাইজান,আলজিরিয়া ও ত্রিপলিতে এই সময় ইসলামের পতাকা উড্ডীন হয়। বস্তুতঃইহার পূর্বে যেমন এরূপ দেশ জয়ের কোন দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয় নাই, তেমনি ইহার পরেও নয়। তাঁহার নিক্ষিপ্ত কোন তীরই লক্ষ্যভেদে ব্যর্থ হয় নাই। তাঁহার উন্নত করা কোন ঝাণ্ডাই কখনো অবনমিত হয় নাই।
মুসলিমদের জীবন ছিল তাঁহার নিকট সর্বাধিক প্রিয় বস্তু। তিনি এমন সব লোককে সেনাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিতেন, সমসাময়িক সমাজে জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিচক্ষণতায় যাঁহাদের বিশেষ মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত ছিল। ‘নেহাওন্দ’ যুদ্ধে তিনি নু’মান বিন মাকরানকে লিখিয়াছিলেনঃ
আমি জানিতে পারিয়াছি যে, নেহাওন্দ শহরে অমুসলিম দুশমনগণ তোমাদের সহিত সংঘর্ষ বাধাইবার জন্য দলে দলে সমবেত হইতেছে। আমার এই চিঠি পাওয়া মাত্রই তোমার নিকটবর্তী মুসলিমগণকে লইয়া আল্লাহ্র আদেশ, সাহায্য ও রহমতের ছায়ায় যাত্রা করিবে। তাহাদিগকে বন্ধুর ও দুর্গম পথে লইয়া যাইবে না। কেননা উহাতে তাহাদের বিশেষ কষ্ট হইবে। তাহাদের সঙ্গত কোন অধিকারেই হস্তক্ষেপ করিবে না। অন্যথায় তাহারা অসন্তুষ্ট ও বিক্ষুব্ধ হইবে। তাহাদিগকে লইয়া নিবিড় অরণ্য পথেও প্রবেশ করিবে না। জানিয়া রাখিও,একজন মুসলিম ব্যক্তি এক লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা অপেক্ষাও আমার নিকট অধিকতর প্রিয় ও মূল্যবান।
তিনি এই অভূতপূর্ব দেশ জয়ের অভিযানে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য বিভিন্ন যুদ্ধে অসংখ্য সৈন্য প্রেরণ করিয়াছেন; কিন্তু যুদ্ধে কোন সিপাহী কিংবা সিপাহসালারের শাহাদাতের সংবাদ পাইলে তাঁহার দুই চক্ষুকটোর হইতে অবিশ্রান্ত ধারায় মর্মব্যথার তপ্ত অশ্রু বিগলিত হইয়া দরদর বেগে প্রবাহিত হইত, এমন কি সেই সঙ্গে কোন বিরাট দেশ জয়ের শুভ সংবাদ শুনাইলেও তাহা বারণ মানিত না।
হযরত উমর (রা) তাঁহার পূর্ববর্তী দুই মহান ব্যক্তির (রাসূলে করীম ও আবূ বকর সিদ্দীক)-এর মতই ন্যায়পরায়ণতা ও সততার নিশানবরদার ছিলেন। তাঁহার কণ্ঠনিঃসৃত বানীও ছিল তাঁহাদেরই অনুরূপ। বিদ্রোহী কুর্দজাতিকে দমন করার উদ্দেশ্য তিনি মুসলিমা আশজায়ীকে যখন প্রেরণ করেন, তখন তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলেনঃ
আল্লাহ্র নাম লইয়া রওয়ানা হইয়া যাও এবং আল্লাহ্র পথে আল্লাহ্দ্রোহী লোকদের সহিত পূর্ণ শক্তিতে লড়াই কর। তোমাদের মুশরিক ভাইদের সহিত সম্মুখ-সমর সংঘটিত হইতে থাকিলে প্রথমে তাহাদের নিকট তিনটি প্রস্তাব পেশ কর। তাহাদিগকে ইসলাম কবুল করার দাওয়াত দাও। তাহারা ইসলাম কবুল করিলে ও অস্ত্রসংবরণ করিয়া নিজেদের ঘরে বসিয়া থাকিতে প্রস্তুত হইলে তাহাদের ধনসম্পদ হইতে যাকাত আদায় করা তোমাদের কর্তব্য। তাহারা তোমাদের সহিত মিলিত হইয়া কাফিরদের বিরুদ্ধে লড়াই করিতে প্রস্তুত হইলে তাহাদের ও তোমাদের অধিকার ও মর্যাদা সমান হইবে। কিন্তু তাহারা যদি ইসলাম কবুল করিতে অস্বীকার করে,তবে তাহাদের নিকট আনুগত্য ও খারাজ প্রদানের দাবি জানাও। কিন্তু তাহাদের শক্তি-সামর্থের অধিক কোন বোঝা তাহাদের উপর চাপাইয়া দিওনা। খারাজ দিতে প্রস্তুত না হইলে তাহাদের সহিত লড়াই কর। আল্লাহ্ তাহাদের বিরুদ্ধে তোমাদের সাহায্য করিবেন।
হযরত উমর ফারুক (রা) প্রাদেশিক শাসনকর্তা ও বিভিন্ন বিভাগীয় সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে বিন্দুমাত্র আরামপ্রিয়তা, বিলাসিতা ও জাঁকজমক বরদাশত করতে প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি শাসক ও শাসিতের মধ্যে পূর্ণ ঐক্য ও সমতা রক্ষার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেন। অনারবদের বিলাসী সভ্যতা ও উচ্ছৃখল চরিত্র যেন তাহাদিগকে স্পর্শ করিতে না পারে, সেজন্য তাঁহার সংরক্ষণমূলক প্রচেষ্টার অন্ত ছিল না। শাসনকর্তা হযরত উৎবা বিন ফরকাদ (রা)- কে তিনি স্পষ্ট ভাষায় লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেনঃ বিলাসিতা, জাকঁজমক, সুখসম্ভোগ, মুশরিকী আচার ও রীতিনীতি এবং রেশমী বস্ত্র পরিহার করিয়া চলিবে।
নবনিযুক্ত শাসনকর্তাদের নিকট হইতে তিনি এই মর্মে প্রতিশ্রুতি গ্রহন করিতেন যে, তুর্কি ঘোড়ায় আরোহণ করিবে না, (কেননা ইহা তখনকার সময় চরম বিলাসিতারুপে বিবেচিত হইত), দ্বাররক্ষী নিযুক্ত করিবে না, অভাবগ্রস্ত ও প্রয়োজনশীল লোকদের জন্য দ্বার সতত উন্মুক্ত ও অবাধ রাখিবে। কেহ ইহার বিরুদ্ধাচরণ করিলে তিনি অনতিবিলম্বে তাহাকে পদচ্যুত করিতেন।
হযরত সায়াদ কুফা নগরে এক বিরাট প্রাসাদ নির্মাণ করেন। হযরত উমর (রা) উহাকে অগ্নি-সংযোগ করিয়া ভস্ম করিয়া ফেলেন। মিশরে হযরত খারেজা বিন হাজাফা এক বালাখানা তৈয়ার করেন। সংবাদ পাইয়া হযরত উমর (রা) উহাকে ধ্বংস করার নির্দেশ পাঠান। কেননা অন্যান্য অবৈধতা ছাড়াও উহার ফলে প্রতিবেশীর পর্দা বিনষ্ট হওয়ার আশংকা দেখা দিয়াছিল।(কিতাবুল খারাজ)
হজ্জের সময় মক্কা শরীফে উপস্থিত হইয়া উমর ফারুক (রা)শাসনকর্তাদের বিরুদ্ধে কোন প্রকার অভিযোগ থাকিলে তাহা সরাসরি তাঁহার নিকট পেশ করার আহবান জানাইয়া সাধারণ ঘোষণা প্রকাশ করিতেন। এক ব্যক্তি কোন শাসনকর্তার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করিল যে, সে তাহাকে অকারণ একশত চাবুকের আঘাত দিয়াছে। উত্তরে তিনি বলিলেন, সংশ্লিষ্ট শাসনকর্তাকে তুমি একশত চাবুক মারিবে।বস্তুত ইহা যে কত বড় কঠিন ফয়সালা, তাহা সহজেই অনুমেয়। সংশ্লিষ্ট শাসনকর্তা ইহাতে শিহরিয়া উঠিল। সে দাঁড়াইয়া বলিলঃ ‘এইরূপ করিলে শাসনকর্তার মর্যাদা নষ্ট হইবে ও শাসনকার্য অচল হইয়া যাইবে’। হযরত উমর (রা) বলিলেনঃ “তৎসত্ত্বেও এইরুপ সুবিচারের দৃষ্টান্ত স্থাপন অপরিহার্য কেননা স্বয়ং নবী করীম (স) এইরূপই করিয়াছেন’।
হযরত খালিদ ইবনে অলীদ (রা) কোন জাতীয় ও সামগ্রিক প্রয়োজন ব্যতীতই বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করিয়াছেন জানিতে পারিয়া হযরত উমর (রা)তাঁহাকে পদচ্যুত করার ফরমান প্রেরণ করেন। তিনি বলেনঃ “খালিদ এই অর্থ নিজ হইতে ব্যয় করিলে নিঃসন্দেহে অর্থের অপচয় করিয়াছেন আর বায়তুলমালের অর্থ ব্যয় করিয়া থাকিলে অনধিকার চর্চা ও আমানতে খিয়ানত করিয়াছেন”।
হযরত উমর (রা) পূর্ববর্তী মহান ব্যক্তিদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াই খিলাফতের কার্য সম্পাদন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেনঃ “আমার দুই সাথী ইতিপূর্বে অতীত হইয়াছেন। একই পথ ও পন্থাই তাঁহারা অবলম্বন করিয়াছিলেন। আমি তাঁহাদের বিপরীত কাজ করিলে তো আমার পক্ষে সম্পূর্ণ ভিন্ন পথ অবলম্বন করা হইবে”। বস্তুতঃ ইহা বিশ্বনবীর এই কথারই প্রতিধ্বনি মনে হয়ঃ ‘আমার পর কেহ নবী হইলে উমরই হইতেন সেই নবী’।
উমর ফারুক (রা)-এর চরিত্রে যে কঠোরতা ও অনমনীয় ভাবধারা পরিলক্ষিত হয়, স্বয়ং নবী করীম (স)-ই ইহার সঠিক ব্যাখ্যা দান করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেনঃ ‘আল্লাহ্র কার্যসমূহে উমর যত শক্ত ও কঠোর, আমার উম্মতের মধ্যে তত আর কেহ নয়’।
অপর একজন বলেন, ‘উমর সত্যের জন্য দানশীল; কিন্তু অন্যায় ও বাতিলের জন্য হাড়ে হাড়ে কৃপণ’।
বস্তুত হযরত উমর (রা) প্রকৃতির অন্ধ দাস ছিলনে না; তিনি কোন ব্যাপারে নিছক প্রকৃতিগত কঠোরতার দরুণই কঠোরতা অবলম্বন করিতেন, একথা কিছুমাত্র সত্য নহে; বরং কঠোরতা ও কোমলতা সম্পর্কে তাঁহার ধারণা অত্যন্ত সুস্পষ্ট ছিল, এ ব্যাপারে তাহার মন ও মগজ ছিল সর্বদা জাগ্রত। তাই তিনি নিজেই স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করিয়াছেনঃ
খিলাফতের কার্য যথাযথরূপে সম্পন্ন হইতে পারেনা যতক্ষণ না এমন কঠোরতা অবলম্বন করা হইবে, যাহা জুলুমের পর্যায় গিয়া পৌঁছায় না। এমন বিষয়েও নম্রতা অবলম্বিত হওয়া উচিত নহে, যাহার ভিত্তি দুর্বলতার উপর স্থাপিত। (কিতাবুল খারাজ)
আর এই কঠোরতাও ছিল সম্পূর্ণরূপে শরীয়াতের ব্যাপারে-আল্লাহ্র হক ও বান্দাহর হক-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু ব্যক্তিগত ব্যাপারে হযরত উমর (রা) কোন দিনই এক বিন্দু কঠোরতা প্রদর্শন করেন নাই। বরং সে ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন মোম অপেক্ষাও দ্রবীভূত ও কোমল। ঠিক এই কথাই জানা যায় উমর ফারুক (রা)-এর নিজের এক ভাষণ হইতে। তিনি প্রসঙ্গত বলিয়াছেনঃ
******(আরবী)
আল্লাহ্র শপথ, আমার দিল আল্লাহ্র ব্যাপারে যখন নরম হয়, তখন পানির ফেনা অপেক্ষাও অধিক নরম ও কোমল হইয়া যায়। আর আল্লাহ্র দ্বীন ও শরীয়াতের ব্যাপারেই (প্রয়োজন মুতাবিক) যখন শক্ত ও কঠোর হয়, তখন তাহা প্রস্তর অপেক্ষাও অধিক শক্ত ও দুর্ভেদ্য হইয়া পড়ে।
বস্তুত খিলাফতের দায়িত্ব সম্পাদনের ব্যপারে হযরত উমর ফারুক (রা) যে কঠোর নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা রাষ্ট্রনীতির দৃষ্টিতে ছিল একান্তই অপরিহার্য। হযরত খালিদ ইবনে অলীদকে পদচ্যুতকরণ, শাসনকর্তাদের সহিত কঠোরতা অবলম্বন, ইসলামী বিধান পালনে অত্যন্ত কড়াকড়ি অবলম্বন প্রভৃতি ক্ষেত্রে হযরত উমর (রা)-এর খিলাফতেরই ন্যায় বিরাট দায়িত্ব পাওনের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তিনি যাহা কিছু করিয়াছেন, খলীফা পদের কঠিন দায়িত্ব পালনের জন্যই করিয়াছেন। কেননা তাহা না করিলে খিলাফতের ন্যায় অতিশয় নাজুক ও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব কিছুমাত্র পালিত হইতে পারিত না। আর আল্লাহ্ না করুন, হযরত উমরও যদি খিলাফতের দায়িত্ব পালন করিয়া ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার বাস্তব নিদর্শন প্রতিষ্ঠা না করিতেন, তাহা হইলে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার বিলুপ্তিই ছিল অবধারিত।
তবে খিলাফতের দায়িত্ব পালনে তাঁহার কঠোরতা, অনমনীয়তা ও ক্ষমাহীনতা উমর চরিত্রের একটি দিকমাত্র। উহারই অপর দিকে হইল দয়া, সহানুভূতি ও ক্ষমা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে তাঁহার দৃষ্টান্তহীন অবদান। তদানীন্তন সমাজে আল্লাহ্র বিবেক-সম্পন্ন সৃষ্টিকুলের মধ্যে ক্রীতদাসদের তুলনায় অধিক দয়া ও সহানুভূতি লাভের অধিকারী আর কেহই ছিল না। হযরত উমর ফারুক (রা) খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহন করার পরই সমস্ত আরব ক্রীতদাসদের সম্পূর্ণ মুক্ত করিয়া দেন। সেই সঙ্গে তিনি এই মর্মে একটি শাসনতান্ত্রিক বিধানও জারী করেনঃ ‘আরববাসী কখনো কাহারো দাস বা গোলাম হইতে পারে না’। তদানীন্তন সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থানুযায়ী সমস্ত অনারব ক্রীতদাসকে মুক্ত করা বড়ই দুরূহ ব্যাপার ছিল। তা সত্ত্বেও তাহাদের পক্ষে কল্যাণকর বহু আইন-বিধান তিনি কার্যকর করেন। এমনকি মনিব-মালিকদের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের জন্যও তিনি সরকারী ভাতা বা বৃত্তি জারী করিয়া দেন।
হযরত উমর (রা) যিম্মী ও অমুসলিমদের সহিত এমন হৃদ্যতাপূর্ণ ও সম্মানজনক আচরণ গ্রহন করিয়াছিলেন, যাহা একালের মুসলমানরাও মুসলমানদের সহিত করেন না। এই ব্যাপারে তিনি জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বিশেষ সচেতন ছিলেন। সেই সঙ্গে তিনি সাধারণভাবে ক্ষমা ও অনুগ্রহ প্রদর্শনও বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করিতেন না।
দ্বিতীয় খলীফা সাধারণ জনকল্যাণমূলক কাজ কেবল সরকারী পর্যায়েই করিতেন, তাহা নয়। তিনি ব্যক্তিগতভাবেও মানবতার কল্যাণে সর্বক্ষণ কর্মে নিরত থাকিতেন। জিহাদের ময়দানে গমনকারী মুজাহিদদের বাড়ি বাড়ি গিয়া তিনি তাঁহাদের পরিবারবর্গের খবরাখবর লইতেন। কাহারো কোন প্রয়োজন দেখা দিলে তিনি সঙ্গে সঙ্গেই তাহা পূরণের ব্যবস্থা করিয়া দিতেন। কোথাও ভূক্ত লোক দেখিতে পাইলে অনতিবিলম্বে তাহাদের খাওয়ার ব্যবস্থা করিয়া দিতেন। উমর ফারুক (রা)-এর খিলাফত আমলে ধনী-দরিদ্র, নিঃস্ব ও ধনাঢ্যের মধ্যে পূর্ণ সমতা ও সাম্য স্থাপিত হইয়াছিল। জনগণের মধ্যে একবিন্দু বৈষম্যমূলক আচরণ প্রদর্শন না করার জন্য দায়িত্বশীল কর্মচারীদের প্রতি তিনি কঠোর নির্দেশ দিয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি নিজে কোনরূপ তোষামোদ ও তারীফ-প্রশংসা পছন্দ করিতেন না। মদীনার বিচারালয়ে তিনি বিবাদী হিসাবে উপস্থিত হইলে বিচারপতি খলিফাতুল মুসলেমীনের সম্মানার্থে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ইহা দেখিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ বলিলেনঃ ‘এই মামলায় ইহাই তুমি প্রথম অবিচার করিলে’। খলীফার দাপট ও প্রতাপে তখন গোটা পৃথিবী কম্পমান ছিল; কিন্তু তাঁহার অবলম্বিত সাম্য নীতির ফলে বিদেশী রাষ্ট্রদূতগণ আমিরুল মুমিনীনকে সহসা চিনিয়া লইতে পারিতেন না। তিনি অত্যন্ত তীব্র সম্ভ্রম বোধসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। পর্দাসংক্রান্ত আয়াত নাজিল হওয়ার পূর্বে সাধারণ মুসলিম মহিলারা তো বটেই,নবী করীম (স)-এর বেগমগণও পর্দা পালন করিতেন না। কিন্তু এই পর্দাহীনতা ও মহিলাদের অবাধ চলাফিরাকে তিনি তখনও পছন্দ করিতে পারিতেন না।
ফারুকী চরিত্রের মৌল ভিত্তি
হযরত উমর ফারুক (রা)-এর সুমহান চারিত্রিক গুণাবলী অত্যন্ত মজবুত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। উন্নততম নৈতিক মান প্রতিষ্ঠাকারী হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর নিবিড় ও ঘনিষ্টতম সাহচর্য হইতেই তিনি এই ভিত্তি অর্জন করিয়াছিলেন। ব্যক্তিগতভাবে তিনি ছিলেন মহৎ গুণাবলীতে বিভূষিত,নবী চরিত্রের বাস্তব প্রতিমূর্তি। তাঁহার চরিত্র-দর্পণে সর্বাধিক মাত্রায় প্রতিফলিত হইয়াছিল একনিষ্ঠতা, আল্লাহ্তে আত্মসমর্পণ, বৈষয়িক স্বাদ আস্বাদনে অনীহা, জিহ্বা ও মনের সংযম, ন্যায়পরায়ণতা, সত্যপরায়ণতা, বিনয় ও অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা। এই মহৎ গুণাবলী তাঁহার চরিত্রে এতই দৃঢ় ছিল যে, কোন লোক তাঁহার সংস্পর্শে আসিলে, তাঁহার চরিত্রেও এই গুণাবলী গভীরভাবে রেখাপাত করিত। তাঁহার নিকট হইতে প্রকৃত তাকওয়া পরহেজগারী শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্য বহু সাহাবীও অতীব উৎসাহে তাঁহার সংস্পর্শ লাভের জন্য চেষ্টিত হইতেন। স্বয়ং রাসূলে করীম (স) তাহার সম্পর্কে বলিয়াছেনঃ
*******(আরবী)
আল্লাহ্ ত’আলা উমরের মুখ ও দিলের উপর সত্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়াছেন। তিনি হইলেন হক্ক বাতিলের মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য বিধানকারী।
ফারুকী খিলাফত কালের সরকারী পদাধিকারীদের চরিত্রেও ইহার প্রভাব পুরামাত্রায় প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল।
আল্লাহ্ ভীতির তীব্রতা
উমর (রা)-এর চারিত্রিক দৃঢ়তার মূল উৎস ছিল আল্লাহ্র কুদরাত ও শক্তিমত্তার প্রতি দৃঢ় প্রত্যয়। তিনি নিতান্ত বিনয় ও ভীত-সন্ত্রস্ত হৃদয় লইয়া গভীর রাত্র পর্যন্ত নামাযে নিরত থাকিতেন। কুরআনের যে সব আয়াতে আল্লাহ্র মহানত্ত ও মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিয়া তিনি ভাবাবেগে অত্যন্ত আপ্লুত হইয়া যাইতেন এবং অদম্য কান্নায় ভাঙ্গিয়া পড়িতেন। তাঁহার হৃদয় এতই কোমল ও আর্দ্রতাপূর্ণ ছিল যে, একবার তিনি ফজরের নামাযে সূরা ইউসুফ পড়িতে শুরু করিলে তাঁহার হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিত এবং কাঁদিতে কাঁদিতেই সমগ্র কুরআন শেষ করিয়া রুকূতে যাইতে বাধ্য হইলেন।
কিয়ামত দিবসের পাকড়াওকে তিনি খুব বেশী ভয় পাইতেন। তিনি প্রায়শঃ বলিতেন, কিয়ামতের দিন জাহান্নামের আযাব হইতে কোনমতে রক্ষা পাইলেও নেকী-বদী সমান-সমান হইলেই আমি নিজেকে বড় সৌভাগ্যবান মনে করিব। একাবার একটি তৃণখণ্ড হাতে লইয়া তিনি দুঃখ-ভারাক্রান্ত কণ্ঠে বলিতে লাগিলেনঃ ‘হায়, আমি যদি এই তৃণখণ্ডের ন্যায় দায়িত্বমুক্ত হইতাম! হায়, আমি যদি ভূমিষ্ঠই না হইতাম! আল্লাহ্র ভয়ে তাঁহার হৃদয়-মন সব সময়ই ভীত-শঙ্কিত হইয়া থাকিত। এইজন্য তিনি প্রায়শঃবলিতেনঃঊর্ধ্বলোক হইতে যদি ঘোষিত হয় যে, দুনিয়ার একজন ছাড়া সমস্ত মানুষই জান্নাতী হইবে, তখনো আমার মনকে এই আশংকা কাতর ও আশংকাগ্রস্ত করিয়া রাখিবে যে, কি জানি, সেই হতভাগ্য ব্যক্তি আমিই না হইয়া পড়ি।
রাসূলের প্রতি ভালবাসা ও আনুগত্য
মন-মানসিকতার পরিচ্ছন্নতা ও পরিশুদ্ধি এবং উত্তম ও অকৃত্রিম চারিত্রিক গুন-বৈশিষ্ট্য অর্জনের জন্য মহৎ চরিত্রের মৌল উৎস বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর প্রতি ঐকান্তিক ভালোবাসা ও তাঁহার সুন্নাত অনুসরণ করিয়া চলার অকৃত্রিম নিষ্ঠা অর্জন একান্তই অপরিহার্য। বস্তুতঃযে দিল রাসূলের প্রতি প্রেমময় নয় এবং যে পদক্ষেপ রাসূলে করীম (স)-এর উত্তম আদর্শানুসারী নয়, তাহা ইহ-পরকালের নিয়ামত লাভে ধন্য হইতে পারে না। হযরত উমর ফারুক (রা) ছিলেন রাসূলের সত্যিকার নিষ্ঠাবান প্রেমিক। তিনি নিজের জান-মাল ও সন্তান-স্বজন অপেক্ষাও অধিক ভালবাসিতেন রাসূলে করীম (স)-কে। এই কারণে তিনি নবী করীম (স)-এর ইন্তেকালের ব্যাপারটিকে সহসা ও সহজভাবে স্বীকার করিয়া নিতে সক্ষম হন নাই।
হযরত উমর (রা) চরিত্রের সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল দিক হইল প্রতিপদে রাসূলে করীম (রা)-এর আক্ষরিক অনুসরণ। পানাহার, পোশাক-পরিচ্ছদ, উঠা-বসা,চলা-ফিরা,কথা-বার্তা প্রভৃতি সর্বকাজে তিনি নবী-আদর্শকে নিষ্ঠার সহিত অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন। রাসূলে করীম (স) অভাব-অনশন ও দারিদ্রের মধ্যে দিয়া জীবন অতিক্রম করিয়াছেন। এই জন্য হযরত উমর (রা) রোম ও পারস্যের বিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতি হইয়াও নিতান্ত দরিদ্রের ন্যায় জীবন অতিবাহিত করিতেন। একবার তাঁহার কন্যা উম্মুল মুমিনীন হযরত হাফসা (রা) বলিয়াছিলেনঃ ‘আল্লাহ্ তা’আলা এখন তো স্বাচ্ছন্দ্য ও প্রাচুর্য দান করিয়াছেন। কাজেই উত্তম পরিচ্ছদ ও উৎকৃষ্ট খাদ্য গ্রহন হইতে এখন আপনার বিরত থাকা উচিত নয়। জওয়াবে তিনি বলিলেনঃ ‘রাসূলে করীমের দুঃখ ও দারিদ্র-জর্জরিত জীবনের কথা কি তুমি ভুলিয়া গেলে? আল্লাহ্র শপথ, আমি তো আমার ‘নেতা’কে অনুসরণ করিয়াই চলিব। .........চলিব এই আশায় যে, পরকালে আল্লাহ্ আমাকে সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য দান করিবেন’।
রাসূলে করীম (স)-কে তিনি যে কাজ যেভাবে করিতে দেখিয়াছেন, সেই কাজটি ঠিক সেইভাবেই সম্পন্ন করিতে সব সময়ই চেষ্টিত থাকিতেন। তাঁহার কাজের ধরণ দেখিয়া উহার কারণ জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি অকপটে বলিয়া ফেলিতেনঃ “আমি রাসূলে করীম (স)-কে এই কাজটি ঠিক এইভাবে করিতে দেখিয়াছি বলিয়াই আমি ইহা এইভাবে করিলাম”।
দায়িত্বের তীব্র অনুভূতি
হযরত উমর (রা) স্বীয় দায়িত্ব ও কর্তব্যের ব্যপারে অত্যন্ত তীব্র অনুভূতিসম্পন্ন ছিলেন। জনগণের সব কিছুর জন্য তিনি নিজেকে দায়ী মনে করিতেন এবং সে দায়িত্ব পালনে যত কষ্টই হউক, তিনি তাহা অকাতরে বরদাশত করিতেন। মুসলিম জনগণ বা রাষ্ট্রের যে সব ধন-সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব তাঁহার উপর অর্পিত হইত, উহার জন্য তিনি চূড়ান্ত মাত্রায় কষ্ট ও শ্রম সহ্য করিতেন। বায়তুল মালের কোনরূপ ক্ষতি সাধিত হইলে তাহা পূরণ করিতেন এবং কোন কিছু হারাইয়া গেলে তাহা খুঁজিয়া বাহির করিতে যত শ্রমেরই প্রয়োজন হইত, ব্যক্তিগতভাবে তাহা স্বীকার করিতে তিনি একবিন্দু কণ্ঠিত হইতেন না।
হযরত আলী (রা) বলেন, একদা আমি হযরত উমর (রা)-কে উষ্ট্রে সওয়ার হইয়া দ্রুত চলিয়া যাইতে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলামঃ আমীরুল মু’মিনীন, আপনি কোথায় যাইতেছেন?’ জওয়াবে তিনি বলিলেনঃ ‘যাকাত বাবদ আদায় করা একটি উষ্ট্র হারাইয়া গিয়াছে, উহার খোঁজ করিতে বাহির হইয়াছি’। আমি বলিলামঃ এইরূপ করিয়া আপনি তো আপনার পরবর্তী খলিফাদের জন্য দায়িত্ব পালন অত্যন্ত কঠিন করিয়া দিতেছেন, অর্থাৎ আপনি খিলাফতের দায়িত্ব পালনে এতখানি কষ্ট স্বীকার করিলে আপনার পরে যাহারা খলীফা হইবেন,তাহাদিগকেও অনুরূপ কষ্ট করিতে হইবে। এই শুনিয়া তিনি বলিলেনঃ
*******(আরবী)
হে হাসানের পিতা! আমাকে তিরস্কার করিও না। যে আল্লাহ্ মুহাম্মাদ (স)-কে নবুয়্যাত দান করিয়া পাঠাইয়াছেন, তাঁহার শপথ; ফোরাত নদীর তীরে একটি উষ্ট্রও যদি মরিয়া যায়, তাহা হইলেও কিয়ামতের দিন সেজন্য এই উমরকেই পাকড়াও করা হইবে।
বস্তুতঃ অপরিসীম দায়িত্ববোধ এবং কিয়ামতের জওয়াবদিহির প্রতি অকৃত্রিম ও অবিচল বিশ্বাস থাকিলেই এইরূপ কথা বলা যায় এবং রাষ্ট্রীয় সম্পদ রক্ষার জন্য অনুরূপ চেষ্টা ও কষ্ট স্বীকার করা সম্ভব ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই।
হযরত উমর (রা) জনগণের প্রকৃত অবস্থা জানিবার জন্য রাত্রিকাল লোকালয়ে চলাফিরা করিতেন। তিনি একই ঘরে পরাপর তিন রাত্রি পর্যন্ত কান্নার ধ্বনি শুনিতে পাইয়াছিলেন। পরে তিনি ঘরে লোকদের ডাকিয়া শিশুর কান্নার কারণ জানিতে চাহিলেন। শিশুর মা বলিলঃ ‘স্তন সেবন বন্ধ না করা পর্যন্ত বায়তুল মাল হইতে শিশুর জন্য বৃত্তি বরাদ্দ করা হইবে না বিধায় অবিলম্বে দুগ্ধপোষ্য শিশুর স্তন সেবন বন্ধ করিতে চেষ্টা করা হইতেছে। শিশুর ইহাই মূল কারণ’।
এই কথা জানিতে পারিয়া অবিলম্বে তিনি ঘোষণা করাইলেনঃ
********(আরবী)
তোমারা শিশুর স্তন পান বন্ধ করার জন্যে তাড়াহুড়া করিও না। অতঃপর আমরা প্রত্যেক মুসলিম সন্তানের জন্যই খাদ্য বরাদ্ধ করিতেছি।
সেই সঙ্গে সমগ্র ইসলামী রাজ্যে এই বিধান অবিলম্বে কার্যকর করার জন্য তিনি স্পষ্ট নির্দেশ পাঠাইলেন।১ {দায়িত্ববোধের অনন্য দৃষ্টান্তঃএই প্রসঙ্গে আরেকটি ঐতিহাসিক ঘটনার কথা এখানে উল্লেখযোগ্য। একদা গভীর নিশিথে খলীফা উমর (রা) ইবনে আব্বাস(রা)-কে সঙ্গে লইয়া মদীনা হইতে দূরবর্তী এক পল্লী এলাকা পরিদর্শনে গেলেন। তাঁহারা একটি মহল্লার ভিতর দিয়া অতিক্রমের সময় পার্শ্ববর্তী জীর্ণ কুটিরের ভিতর হইতে শিশুদের ক্রন্দন-ধ্বনি শুনিতে পাইলেন। তাঁহারা কুটিরের ভিতর উঁকি মারিয়া দেখিলেনঃ এক বৃদ্ধা মহিলা উনুনে পানি ভর্তি হাঁড়ি বসাইয়া আগুন জ্বালাইতেছেন এবং উহার চারিপার্শ্বে বসিয়া শিশুরা ক্ষুধার জ্বালায় ক্রদন করিতেছে। মহিলা কিছুক্ষন থামিয়া থামিয়া শিশুদের প্রবোধ দিতেছেনঃ ‘তোমরা আরেকটু সবুর কর, এক্ষুণি খাবার তৈয়ার হইয়া যাইবে’। কিন্তু শেষ পর্যন্ত খাবার আর তৈয়ার হইল না। অনেক্ষন ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ক্লান্ত হইয়া অবশেষে শিশুরা ঘুমাইয়া পড়িল। মহিলাটিও একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া স্বগতোক্তি করিলঃ ‘যাক, আজিকার রাত্রের মত অন্ততঃ বাঁচা গেল’। এই মর্মান্তিক অবস্থা দেখিয়া খলীফা উমর (রা) এবং তাঁহার সহচর মহিলাটির মুখামুখি হইলেন তাঁহাদের প্রশ্নের জবাবে মহিলাটি, বলিলেনঃ ‘তাঁহার পরিবারে উপার্জনক্ষম কোন পুরুষ সদস্য নাই; তিনি নিজেও উপার্জন করিয়া শিশুদের মুখে অন্ন যোগাইতে পারিতেছেন না। তাই কয়েকদিন যাবত তিনি উনুনে শুধু পানিভর্তি হাঁড়ি বসাইয়া ক্ষুধার্ত শিশুদের এইভাবে প্রবোধ দিতেছেন’। তাঁহার প্রশ্ন করিয়া আরো জানিতে পারিলেন যে, রাষ্ট্রের বায়তুল মাল হইতে এ পর্যন্ত তাহাদের নিকট কোন খাদ্য-সাহায্য পৌঁছে নাই। এই মর্মভেদী কাহিনী শুনিয়া খলীফা এবং তাহার সহচর দ্রুত মদীনা পৌঁছিয়া বায়তুল মালের গুদামের দরজা খুলিলেন। অতঃপর তিনি নিজেই এক বস্তা ময়দা ও একবস্তা চিনি কাঁধে তুলিয়া দরিদ্র মহিলাটির উদ্দেশে রওয়ানা হইলেন। এই সময় ইবনে আব্বাস (রা) অন্ততঃএকটি বস্তা তাঁহার কাঁধে তুলিয়া দেওয়ার জন্য খলিফাকে অনুরোধ করিলেন। খলীফা উহা দ্বীর্থহীন ভাষায় প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিলেনঃ ‘ইবনে আব্বাস! আজ তুমি আমার বোঝা হাল্কা করিবার জন্য আগাইয়া আসিয়াছ;কিন্তু কিয়ামতের দিন যখন দায়িত্ব পালনের যখন দায়িত্ব পালনের এই ব্যর্থতার জন্য আমাকে অভিযুক্ত করা হইবে তখন তো তুমি আমার পাপের বোঝা হাল্কা করিতে আগাইয়া আসিবেনা’। দ্বিতীয় খলীফার দায়িত্ববোধ কত প্রখর ছিল, এই ঘটনা উহার জ্বলন্ত প্রমাণ।– সম্পাদক }
এই মানবিকতা, সহানুভূতি ও পরদুঃখ কাতরতা ইসলামী আদর্শ-ভিত্তিক রাষ্ট্র নায়কদের চরিত্রে প্রকট থাকাই বাঞ্ছনীয়।
হযরত উমর (রা) বস্তুতঃই সমাজের প্রতিটি দুর্বল ও ইয়াতীম ব্যক্তির জন্য স্নেহ-বাৎসল্যপূর্ণ পিতার সমতুল্য ছিলেন। সুবিচার ও ন্যাপরায়নতাই ছিল তাঁহার প্রধান বৈশিষ্ট্য। তিনি স্বাধীনতা ও সাম্যের প্রতি সমান গুরুত্ত স্বীকার করিতেন। ১ {স্বাধীনতার প্রশ্নে আপোষহীনতাঃ মানুষের স্বাধীনতা তথা মৌল মানবাধিকার প্রশ্নে হযরত উমর (রা)-এর মনোভাব ছিল আপোষহীন। কোন যুক্তিগ্রাহ্য ও আইনসঙ্গত কারণ ব্যতীত কাহারো স্বাধীনতা এতটুকু ক্ষুণ্ণ করার তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না। এ ব্যাপারে শাসনকর্তাদের প্রতি ও ছিল তাঁহার কড়াকড়ি নির্দেশ। এতৎসত্ত্বেও একবার খলীফার নিকট মিশরের শাসনকর্তার বিরুদ্ধে এই মর্মে অভিযোগ আসিল যে, তিনি (শাসনকর্তা) কোন যুক্তিগ্রাহ্য ও আইনসম্মত কারণ ছাড়াই নেহায়েত সন্দেহের বশে কতিপয় ব্যক্তিকে কারাগারে আটক করিয়া রাখিয়াছেন।খলীফা অবিলম্বে শাসনকর্তাকে ডাকাইয়া আনিয়া ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। শাসনকর্তা ইহার কোন সদুত্তর দিতে পারিলেন না। তখন খলীফা তাহাকে তিরস্কার করিয়া বলিলেনঃ ‘এই লোকগুলিকে তো ইহাদের মায়েরা স্বাধীনভাবেই প্রসব করিয়াছিল। তুমি ইহাদের পরাধীন করিয়া রাখার অধিকার কোথায় পাইলে?’ বস্তুতঃ জীবনের শেষ মুহূর্ত অবধি এই বলিষ্ঠ নীতিভঙ্গির উপরই খলীফা উমর (রা) অবিচল ছিলেন। ইহা হইতে কেহ তাঁহাকে একবিন্দু টলাইতে পারে নাই।–সম্পাদক}
সমাজের দুর্বল ও মিসকীনদের কাতারে দাঁড়াইয়া তিনি মানব জাতির সার্বিক কল্যাণের জন্য কাজ করিতেন। কেবল মুসলমানেরা প্রতিই তাঁহার এই নীতি কার্যকর ছিল না। ইসলামী রাজ্যের অনুগত অমুসলিম নাগরিকদের প্রতিও তিনি বিন্দুমাত্র পার্থক্যবোধ রাখিতেন না। তিনি তাহাদের প্রতি সুবিচারপূর্ণ আচরণ ও ন্যায়নীতি অনুসরণ করার জন্য সকল পর্যায়ের প্রশাসকদের প্রতি নির্দেশ জারী করিয়াছিলেন। তাহাদের প্রতি সকল প্রকার অন্যায় ও জুলুমমূলক আচরণ পরিহার করার জন্য তিনি তাকীদ করিতেন। এই পর্যায়ে তাঁহার নিজেরই একটি ঐতিহাসিক উক্তি বিশেষভাবে উল্লেখ্য।তিনি বলিয়াছিলেনঃ
********(আরবী)
আল্লাহ্ তা’আলা আমার উপর যে দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছেন, তাহার কল্যাণ প্রধানতঃ তিনটি জিনিসের উপর নির্ভরশীল। তাহা হইলঃ আমানত বা বিশ্বস্ততা যথাযথভাবে রক্ষা করা, শক্তি সহকারে উহা ধারণ করা এবং আল্লাহ্র নাজিলকৃত বিধান অনুযায়ী শাসন ও বিচার কার্য সম্পাদন করা।
রাষ্ট্রীয় ধনমাল সম্পর্কে তিনি বলিয়াছিলেনঃ
*******(আরবী)
তোমরা জানিয়া রাখ, এই রাষ্ট্রীয় ধন-মালের কল্যাণ মাত্র তিন প্রকার ব্যবহারে নিহিতঃ উহা গ্রহণ করা হইবে হক্কভাবে- হক্ক অনুসারে, দেওয়া হইবে হক্কভাবে অর্থাৎ হক্ক আদায় স্বরূপ এবং বাতিল পন্থায় গ্রহন বা দান বন্ধ। দুর্বল ঈমানদার লোকের পক্ষে শাসন-বিচারে সুবিচার বাস্তবায়িতকরণই যথেষ্ট।
বিচার কার্যে তিনি সুবিচার প্রতিষ্ঠার জন্য কায়মনোবাক্যে প্রস্তুত হইতেন। দুই বিবদমান পক্ষ বিচার পাওয়ার উদ্দেশ্যে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে তিনি দুই হাঁটু বিছাইয়া মহান আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করিতেন এই বলিয়াঃ
হে আল্লাহ্, তুমি এই কাজে আমাকে সাহায্য কর। কেননা পক্ষদ্বয়ের প্রত্যেকেই আমাকে আমার দ্বীন হইতে বিভ্রান্ত করিয়া দিতে পারে।–(যদি আমি ন্যায়বিচার না করি)।
ভোগ-বিলাসে অনীহা ও অল্পোতুষ্টি
বৈষয়িক স্বাদ-আস্বাদনের লোভ-লালসাই প্রকৃতপক্ষে অনৈতিকতা চরিত্রহীনতা ও দুর্নীতি সৃষ্টির মূল কারণ। এই জন্য হযরত উমর ফারুক (রা) স্বভাবতঃই উহা ঘৃণা করিতেন।তাঁহার সমসাময়িক লোকেরা একবাক্যে স্বীকার করিতেন যে, ভোগ-বিলাসে অনীহা ও অল্পে তুষ্টির ক্ষেত্রে তিনি সকলকে ছাড়াইয়া গিয়াছেন। রাসূলে করীম (স) কোন সময় তাঁহাকে কিছু দিতে চাহিলে তিনি বলিতেনঃ “হে রাসূল! আমার চেয়ে অভাবগ্রস্ত লোক অনেক রহিয়াছে। তাহারাই ইহা পাইবার অধিক যোগ্য”। হযরত উমর (রা)-এর দেহ কখনও নরম মসৃণ পোশাক স্পর্শ করে নাই। খণ্ড খণ্ড তালিযুক্ত কোর্তা,জীর্ণ-দীর্ণ কাপড়ের পাগড়ী, এবং ছিন্ন-চূর্ণ জুতা-ইহাই ছিল তাঁহার আজীবনের ভূষণ। ইহা লইয়াই তিনি কাইজার ও কিসরার রাষ্ট্রদূতদের এবং দেশ-বিদেশের প্রতিনিধিবর্গের সহিত সাক্ষাত করিতেন। তাঁহার নিকৃষ্ট মানের খাবার দেখিয়া লোকেরা স্তম্ভিত ও হতবাক হইয়া যাইত। তিনি বলিতেনঃ ‘তোমরা কি মনে কর আমি উৎকৃষ্ট ও সুস্বাদু খাবার গ্রহনে অক্ষম ও অনিচ্ছুক?আল্লাহ্র শপথ, কিয়ামতের দিবসের ভয় না হইলে আমিও তোমাদের ন্যায় ভোগ-বিলাস ও স্বাদ-আস্বাদনে নিমগ্ন হইতাম’। তিনি সরকারী দায়িত্তে নিযুক্ত কর্মচারীদিগকেও অনুরূপ ভোগ-বিলাস ও স্বাদ-আস্বাদন হইতে বিরত থাকার জন্য কড়া নির্দেশ দিতেন।
অল্পেতুষ্টি ছিল তাঁহার স্বভাবগত গুন। খলীফা নিযুক্ত হওয়ার পর ক্রমাগত কয়েক বৎসর পর্যন্ত তিনি বায়তুলমাল হইতে একটি মুদ্রাও গ্রহণ করেন নাই।অথচ অভাব-অনটন ও দারিদ্রের কষাঘাতে তাঁহার গোটা পরিবারই বিধ্বস্ত হইয়া যাইতেছিল। সাহাবায়ে কিরাম তাঁহার এই অবস্থা দেখিয়া অতি সাধারণ খাদ্য ও পোশাক সংগ্রহ হইতে পারে এমন পরিমাণ ভাতা বায়তুল মাল হইতে তাঁহাকে প্রদানের ব্যবস্থা করিয়া দেন। কিন্তু হযরত উমর (রা) উহা গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন এই শর্তে যে, ‘যতদিন প্রয়োজন ঠিক ততদিনই ভাতা গ্রহন করিতে থাকিব। আমার নিজের আর্থিক অবস্থা সচ্ছল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উহা লওয়া বন্ধ করিয়া দিব’। তখন রুবাই ইবনে জিয়াদ হারেমী বলিলেনঃ ‘আমীরুল মু’মিনীন! আল্লাহ্ তা’আলা আপনাকে যে মর্যাদা দান করিয়াছেন, তাহাতে আপনি দুনিয়ার সকলের অপেক্ষা অধিক বিলাস-ব্যসন, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও আনন্দ-স্ফূর্তির জীবন যাপনের অধিকারী’। হযরত উমর (রা)ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেনঃ ‘আমি তো জনগণের আমানতদার মাত্র। আমানতের খিয়ানত করা কি কখনো জায়েয হইতে পারে?’ হযরত উৎবা(রা) একদিন তাঁহাকে নিকৃষ্ট মানের খাদ্য খাইতে দেখিয়া বলিলেনঃ আমীরুল মু’মিনীন! খাওয়া-পরার ব্যাপারে আপনি যদি কিছুটা বেশী পরিমাণ ব্যয় করেন, তাহাতে মুসলমানদের সম্পদ কম হইয়া যাইব না’। হযরত উমর (রা)বলিলেনঃ ‘বড়ই দুঃখের বিষয়, তুমি আমাকে বৈষয়িক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও বিলাস-ব্যসনে প্রলোভিত করিতেছ’।
বস্তুত খিলাফতের দায়িত্ব অর্পিত হওয়ার পর হযরত উমর (রা)জীবন যাত্রার ব্যাপারে অত্যধিক সতর্কতা অবলম্বন করেন। কেননা এই সময় তাঁহার সামান্য ভুল-ত্রুটি প্রকাশ পাইলেও উহা সমগ্র মুসলিম জনতার চরিত্রে দুর্নীতি প্রশ্রয় পাওয়ার কারণ হইয়া দাঁড়াইতে পারিত।
হযরত উমর ফারুক (রা)-এর খিলাফত
হযরত উমর ফারুক (রা)-এর দশ বৎসরকালীন শাসন আমলে ইসলামী খিলাফত চরম উৎকর্য ও অদৃষ্টপূর্ব অগ্রগতি লাভ করে। রোম ও পারস্যের ন্যায় শক্তিশালী রাষ্ট্রদ্বয় এই সময়ই মুসলমানদের অধিকারভুক্ত হয়। বস্তুতঃমুষ্টিমেয় মরুবাসী অতি অল্প সময়ের মধ্যে যে বিপ্লব সৃষ্টি করিয়াছিল, ইতিহাস উহার দৃষ্টান্ত পেশ করিতে অক্ষম। আলেকজান্ডার দি গ্রেট, চেঙ্গিস খান ও তৈমূর লং সমগ্র পৃথিবী গ্রাস করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছিলেন এবং ভূ-পৃষ্ঠকে তাঁহারা তছনছ করিয়া দিয়াছিলেন; কিন্তু দ্বিতীয় খলীফার আমলের দেশজয় ও রাজ্যাধিকারের সহিত উহার কোন তুলনা হইতে পারে না। প্রথমোক্ত ব্যক্তিগণ এক সর্ব-বিধ্বংসী ঝড়ের ন্যায় একদিক হইতে উথিত হইয়া অত্যাচার-নিষ্পেষণ ও রক্তপাতের সয়লাব সৃষ্টি করিয়া অন্যদিকে চলিয়া গিয়াছেন। আলেকজান্ডার সিরীয় রাজ্যর “ছুর” নগর অধিকার করিয়া এক সহস্র নাগরিক নির্মমভাবে হত্যা করেন। সেই সঙ্গে তিনি ত্রিশ সহস্র নাগরিককে দাস-দাসীতে পরিণত করিয়া বিক্রয় করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই।
কিন্তু হযরত উমর ফারুক (রা)-এর আমলে যে সব দেশ ও শহর-নগরের উপর ইসলামী খিলাফতের পতাকা উত্তোলিত হয়, সেইসব স্থানে জুলুম-নিষ্পেষণ ও নির্যাতনের একটি দৃষ্টান্তও খুঁজিয়া পাওয়া যাইতে পারে না। ইসলামী সৈন্যবাহিনী বিশেষভাবে আদিষ্ট হইয়াছিল এই জন্য যে, তাহারা যেন শিশু, বৃদ্ধ ও নারীর উপর কোন প্রকার হস্তক্ষেপ না করে। ব্যাপক ও সাধারণ নরহত্যা তো দূরের কথা,সবুজ-শ্যামল বৃক্ষরাজি পর্যন্ত কর্তন করাও ইসলামী সেনাদের জন্য কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ছিল। মুসলিম শাসকগণ বিজিত অঞ্চলে ইনসাফ,ন্যায়পরায়ণতা ও সৌজন্যের যে অপূর্ব দৃষ্টান্ত স্থাপন করিতেন, তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া সকলেই মুগ্ধ ও আকৃষ্ট হইত। ফলে ইসলামী খিলাফতী শাসনকে তাহার অপূর্ব রহমত বলিয়া মনে করিত এবং এই রহমত অবিলম্বে তাহাদের দেশ ও জাতির উপর বর্ষিত হইবার জন্য তাহারা রীতিমত প্রার্থনা করিত। এমনকি, তাহারা কৃতজ্ঞতার আতিশয্যে বিজয়ী মুসলমানদিগকে বিশেষ সাহায্য ও সহযোগিতা করিতেও কুণ্ঠিত হইত না। সিরিয়া বিজয়ের ব্যাপারে স্বয়ং সিরিয়াবাসী অমুসলিম জনগণই স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া মুসলমানদের পক্ষে সংবাদ সরবরাহ ও খোঁজ-খবর দেওয়ার কাজ করিয়াছেন। ইরাক বিজয়-কালে তথাকার অনারব জনতা ইসলামী সৈনিকদের জন্য স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া পুল নির্মাণ করে এবং প্রতিপক্ষের গোপন তথ্যাদি সংগ্রহ করিয়া পরিস্থিতির মুকাবিলা করিবার জন্য প্রস্তুত হইবার সুযোগ দেয়। এই সকল পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে হযরত উমর ফারুক (রা)-এর সহিত আলেকজান্ডার দি গ্রেট ও চেংগীজ খানের মত রক্তপাতকারীদের যে কোন তুলনাই হইতে পারে না,তাহা বলাই বাহুল্য।
আলেকজান্ডার ও চেংগীজের রক্তপাত হয়ত তদানীন্তন সমাজে সাময়িকভাবে কোন ফল দান করিয়া থাকিতে পারে; কিন্তু যে রাষ্ট্রের বুনিয়াদই স্থাপিত হয় অত্যাচার-নিষ্পেষণ ও রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের উপর,তাহা সাধারণভাবে মানব সমাজের জন্য কোন স্থায়ী কল্যাণ বহন করিয়া আনিতে পারে না, তাহা নিঃসন্দেহে। বিশেষতঃউল্লেখিত ঘটনাবলির প্রেক্ষিতে এই কথাটি পুরাপুরি প্রযোজ্য হইতে পারে। বর্তমানে এইসব বিশ্ববিজয়ী বীরদের নাম-নিশানা পর্যন্ত কুত্রাপি পরিলক্ষিত হয় না। কিন্তু উমর ফারুক (রা) যে সুবিশাল ইসলামী-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, সুবিচার, ইনসাফ, সহনশীলতা, সাম্য ভ্রাতৃত্ব, উদারতা ও সহানুভূতির মহত গুণরাজি তাহাতে পূর্ণমাত্রায় বিকশিত হইয়াছিল। এই কারণে বিশ্ব-ইতিহাসে ফারুকী খিলাফত যথার্থই এক স্বর্ণ-যুগ ও মানবতার প্রকৃত কল্যাণের যুগে বলিয়া অভিহিত হইতেছে।
খিলাফতের রাষ্ট্র-রূপ
ইসলামের খিলাফতী শাসন ব্যবস্থা যদিও হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর সময় হইতেই সূচিত হয় এবং তাঁহার সংক্ষিপ্ত শাসনকালে ইহার ভিত্তি রচনা করা হয়; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর ফারুক (রা) এর সময়ই সূচিত হয় একটি সুষ্ঠু ও সুসংবদ্ধ রাষ্ট্রব্যবস্থা। এই সময়ই খিলাফতের বিকশিত রূপ বিশ্ববাসীকে মুগ্ধ ও আকৃষ্ট করে। তাঁহার আমলে কাইসার ও কিসরার বিরাট রাষ্ট্রদ্বয়ই যে মুসলমানদের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল তাহাই নয়, সেই সঙ্গে ইসলামী খিলাফতী রাষ্ট্র ও সরকার নিজ নিজ মর্যাদা ও দায়িত্ব সহকারে পূর্ণমাত্রায় কার্য সম্পাদনের সুযোগ লাভ করে। বস্তুতঃএকটি আধুনিক উন্নত রাষ্ট্রের যতগুলি দিক ও বিভাগ থাকিতে পারে, ফারুকী খিলাফতে উহার প্রায় সব কয়টিই যথাযথরূপে বর্তমান ছিল।
হযরত উমর (রা)-এর খিলাফতকালে পাক-ভারত উপমহাদেশের সীমান্ত হইতে মিশর ও সিরিয়া পর্যন্ত সমগ্র এলাকার উপর ইসলামী পতাকা উড্ডীন হইয়াছিল। এই বিশাল অঞ্চলে বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন ভাষাভাষী লোক বসবাস করিত। হযরত উমর (রা)-এর ঐকান্তিক প্রচেষ্টা নিয়োজিত ছিল আরব ও অনারব মুসলমানদিগকে সর্বতোভাবে একজাতি ও এক মনা রূপে গড়িয়া তোলার উদ্দেশ্য। ইসলামী জীবন-দর্শন ও ঈমানী ভাবধারা এই বিরাট অঞ্চলের অধিবাসীদিগকে একই সূত্রে গ্রথিত করিয়া দিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাদের গোত্রীয় জীবনের ধারা তখনো পুর্ববৎই উদ্দাম গতিতে প্রবাহিত ছিল। হিংসা-দ্বেষের জাহিলী ভাবধারা কোন কোন ক্ষেত্রে মাথাচাড়া দিয়া উঠিতেও চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু উমর ফারুক (রা)-এর কঠোরতর আদর্শনিষ্ঠা ও নীতিবাদিতা জাহিলিয়াতের স্তূপীকৃত আবর্জনা অপসারিত করিবার জন্য প্রতি মুহূর্ত চেষ্টিত ছিল। হযরত উমর (রা) সমগ্র ইসলামী রাজ্যের অধিবাসীদিগকে একদিল, একমগজ ও এক লক্ষ্যাভিসারী একটি জাতি রূপে গড়িয়া তুলিতে এবং ইসলামের দুশমনদের মুকাবিলায় তাহাদিগকে সুসংবদ্ধ ও সংগ্রামমুখর করিয়া গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন। পরন্তু যেসব মুসলমান বিভিন্ন কার্যব্যাপদেশে দুনিয়ার অন্যান্য দেশ ও জাতির মধ্যে গিয়া বসবাস করে, তাহারা যাহাতে নিজেদের বৈশিষ্ট্য ও সান্তত্র্য নষ্ট করিয়া ভিন্ন জাতির সহিত মিলিয়া একাকার হইয়া না যায়, সেদিকে তাহার সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল। তিনি সমগ্র আরব দেশকে ইসলাম-দুশমন লোকদের পঙ্কিলতা হইতে সম্পূর্ণ পবিত্র করিয়া তোলেন। তিনি তাঁহার বিশেষ দূরদৃষ্টির ফলে ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার বুনিয়াদ সুদৃঢ়করণ ও মুসলমানদের অর্থনৈতিক উন্নতি বিধানের জন্য কৃষিব্যবস্থার সংস্কার ও উন্নয়ন সাধন করেন। এই জন্য তিনি ইসলামী রাষ্ট্রের মধ্যে কৃষিজমির ক্রয়-বিক্রয় ও বিলি-বিতরণ বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত ভিন্ন জাতির চাল-চলন, রীতি-নীতি ও সভ্যতা-সংস্কৃতি গ্রহন করা সম্পর্কে তিনি মুসলমানদিগকে সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন। তাহাদের জীবন রাসূলে করীম (স)-এর জীবন অনুসারে গড়িবার জন্য সাধারনভাবেই তিনি সকলকে উপদেশ ও নির্দেশ দিতেন
ফারুকী খিলাফতের কাঠামো
হযরত উমর ফারুক (রা)-এর খিলাফত ছিল পূর্ণ মাত্রায় একটি গন-অধিকার-ভিত্তিক রাষ্ট্র। তাঁহার আমলে দেশের যাবতীয় সমস্যা মজলিসে শু’রার সম্মুখে পেশ করা হইত। কুরআন সুন্নাহ ও প্রথম খলীফার অবলম্বিত রীতিনীতিকে সম্মুখে রাখিয়া প্রতিটি বিষয়ে চূড়ান্ত ফয়সালা করা হইত। মজলিসে শু’রায় কখনো সর্বসম্মতভাবে আর কখনো অধিকাংশ লোকের মতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হইত। নিম্নলিখিত সাহাবীগণ তাঁহার মজলিসে শু’রার প্রধান সদস্য ছিলেনঃহযরত উসমান (রা), হযরত আলি(রা), হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা), হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রা),হযরত উবাই ইবনে কায়াব (রা) ও হযরত জায়েদ ইবনে সাবিত (রা)।
এই মজলিসে শু’রা ব্যতীত একটি সাধারণ মজলিসও তাঁহাকে পরামর্শদান ও রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মীমাংসার জন্য বর্তমান ছিল। মুহাজির ও আনসারদের সকল সাহাবী ছাড়াও গোত্রীয় সরদারগণও ইহাতে যোগদান করিতেন। বিশেষ গুরুত্ববহ ও সংকটপূর্ণ মুহূর্তে এই সাধারণ মজলিসের অধিবেশন আহ্বান করা হইত। অন্যথায় দৈনন্দিন কার্য সম্পাদনের জন্য কেবলমাত্র মজলিসে শু’রার ফয়সালার উপরই তাঁহাকে নির্ভর করিতে হইত এবং উহার ফয়সালাই চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইত। এই মজলিসদ্বয় ব্যতীত আরো একটি মজলিস তখন কার্যরত ছিল, যাহাকে ‘মজলিসে খাস’ বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। ইহাতে কেবলমাত্র মুহাজির সাহাবিগণই যোগদান করিতেন।
গণ-অধিকারসম্মত রাষ্ট্র বলিতে সেই ধরণের রাষ্ট্র-সরকার বুঝায়, যেখানে প্রতিটি নাগরিকই তাহার যাবতীয় অধিকার ভোগের সুযোগলাভ করিতে পারে;যেখানে প্রত্যেকই নিজস্ব মতামত প্রকাশ করিতে ও অন্যদের জানাইতে পারে। হযরত উমর (রা)-এর খিলাফতে এই সকল বৈশিষ্ট্য পুরামাত্রায় কার্যকর ছিল। সেখানে প্রতিটি ব্যক্তিই পূর্ণ স্বাধীনতা সহকারে নিজ নিজ অধিকার দাবি করিতে পারিত।
হযরত উমর ফারুক (রা) খলীফা নির্বাচিত হওয়ার পর তাঁহার খিলাফতের মৌল-নীতিমালা ঘোষণা করিয়া যে গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দান করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছিলেনঃ
*********(আরবী)
তোমাদের ধন-সম্পদে আমার অধিকার ততটুকু যতটুকু অধিকার স্বীকৃত হয় ইয়াতীমের মালে উহার মুতাওয়াল্লীর জন্য। আমি যদি ধনী ও সচ্ছল অবস্থায় থাকি, তবে আমি কিছুই গ্রহন করিব না আর যদি গরীব হই, তবে প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী জরুরী পরিমাণ গ্রহন করিব। ১ {অপর একটি বর্ণনার ভাষা এই ****(আরবী) ‘আমি আমার নিম্নতম প্রয়োজন গ্রহন করিব’।}
হে লোকসকল, আমার উপর তোমাদের কতকগুলি অধিকার রহিয়াছে, আমার নিকট হইতে তাহা আদায় করা তোমাদের কর্তব্য। প্রথম, দেশের রাজস্ব ও গণিমতের মাল যেন অযথা ব্যয় হইতে না পারে, দ্বিতীয় তোমাদের জীবিকার মান-উন্নয়ন ও সীমান্ত সংরক্ষণ আমার কর্তব্য। আমার প্রতি তোমাদের এই অধিকারও রহিয়াছে যে, আমি তোমাদিগকে কখনও বিপদে নিক্ষেপ করিব না।
অপর এক ভাষণে তিনি বলিয়াছেনঃ ‘তোমাদের যে কেহ আমার মধ্যে নীতিবিচ্যুতি দেখিতে পাইবে, সে যেন আমাকে সঠিক পথে পরিচালিত করিতে চেষ্টা করে’। উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দের মধ্য হইতে একজন দাঁড়াইয়া বলিলঃ ‘আল্লাহ্ শপথ, তোমার মধ্যে আমার কোন নীতিবিচ্যুতি দেখিতে পাইলে এই তীব্রধার তরবারি দ্বারা উহাকে ঠিক করিয়া দিব’।
হযরত উমর (রা) এই জওয়াব শুনিয়া শোকর আদায় করিলেন ও বলিলেনঃ ‘আল্লাহ্ এই জাতির মধ্যে এমন লোক তৈয়ার করিয়াছেন,যাহারা তাঁহার নীতিবিচ্যুতির সংশোধন করিতে পারেন। এই জন্য আমি আল্লাহ্র শোকর আদায় করিতেছি’।
এই ভাষণ কতকগুলি আকর্ষণীয় শ্লোগান তেজব্যঞ্জক শব্দেরই সমষ্টি নহে; বস্তুতঃইহাই হইতেছে ইসলামী খিলাফতের মেনিফেষ্টো বা নীতিমালা। খলীফা ফারুকে আযম (রা) এই নীতিমালা খুব দৃঢ়তা সহকারেই পালন করিতেন। তাই দেখা যায় আমীরুল মু’মিনীন অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন; কিন্তু ঔষধ হিসাবে ব্যবহার করার জন্য বায়তুল মাল হইতে সামান্য পরিমাণ মধুও কেবলমাত্র এইজন্য গ্রহণ করিলেন না যে, পূর্বাহ্ণে জনগণের নিকট হইতে উহার অনুমতি লওয়া হয় নাই। মসজিদে নববীতে উপস্থিত হইয়া সমবেত জনতার নিকট হইতে প্রকাশ্যভাবে অনুমতি লওয়ার পরই তিনি তাহা গ্রহণ করিতে সম্মত হইয়াছিলেন। পৃথিবীর বড়বড় শাসকদের ইতিহাস অনুরূপ কোন দৃষ্টান্ত পেশ করিতে পারে কি?
হযরত উমর ফারুক (রা) জনগণকে সমালোচনার অবাধ অধিকার প্রদান করিয়াছিলেন। ফলে একজন সাধারণ নাগরিকও খলীফার সমালোচনা করিতে বিন্দুমাত্র পরোয়া করিত না। কেবল পুরুষ নাগরিকগণই এই সুযোগ ভোগ করিতে পারিত তাহা নহে, নারী সমাজও এই ক্ষেত্রে কিছুমাত্র পাশ্চাদপদ ছিল না। স্ত্রীর মোহরানা নির্ধারণ বিষয়ে খলীফা মতের প্রতিবাদ করিয়া যখন একজন স্ত্রীলোক বলিয়া উঠিলঃ ‘হে উমর!আল্লাহ্র ভয় কর,’ তখন উমর ফারুক (রা)ও নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া তাহা পরিহার করেন এবং কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী উক্ত স্ত্রী লোকটির মত অঙ্কুন্ঠিত চিত্তে মানিয়া লইলেন। বস্তুতঃহযরত উমর (রা)-এর খিলাফতের অভূতপূর্ব সাফল্যের মূলে এই ধরণের ইনসাফ ও ন্যায়নীতিই কার্যকর রহিয়াছেন।
ফারুকী খিলাফতের আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা
হযরত উমর (রা) গোটা ইসলামী রাজ্যকে মোট আটটি প্রদেশে বিভক্ত করিয়া লইয়াছিলেন। মক্কা, মদীনা, সিরিয়া, বসরা, কুফা,মিসর ও ফিলিস্তিন। এই কয়টি এলাকা তখন সতন্ত্র ও ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ হিসাবে গণ্য হইত। এতদ্ব্যতীত খোরাসান,আযারবাইজান ও পারস্য এই তিনটি প্রদেশও তাঁহার খিলাফতের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। প্রতিটি প্রদেশের জন্য আলাদাভাবে গভর্নর, বেসামরিক ও সামরিক বিভাগের চীফ সেক্রেটারী, প্রধান কালেক্টর, পুলিশ বিভাগের ডিরেক্টর, প্রধান খাজাঞ্জী, প্রধান বিচারপতি প্রভৃতি উচ্চপদস্থ কর্মচারী নিযুক্ত করা হইয়াছিল।
সাধারণতঃমজলিসে শু’রার পরামর্শক্রমেই এই সব দায়িত্বপূর্ণ পদে লোক নিযুক্ত করা হইত। খলীফার প্রধান কাজ ছিল প্রদেশসমূহের শাসনকর্তাদের প্রতি তীক্ষ্ণ ও সতর্ক দৃষ্টি রাখা এবং তাঁহাদের স্বভাব-চরিত্র ও আদত-অভ্যাসকে ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে গড়িয়া তোলা। খলীফা উমর (রা) এই কাজ বিশেষ দক্ষতা সহকারেই সম্পন্ন করিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন ইসলামী রাষ্ট্রের এক অতন্দ্র প্রহরী। প্রশাসনে ইসলামী আদর্শের একবিন্দু বিচ্যুতি তিনি বরদাশত করিতে মাত্রই প্রস্তুত ছিলেন না। শাসনকর্তা ও দায়িত্বপূর্ণ পদে লোক নিয়োগের সময় তাঁহাদের নিকট হইতে তিনি এই প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিতেন যে তাঁহারা কঠোরভাবে ইসলামী আদর্শ মানিয়া চলিবেন এবং বিলাসিতা অথবা জাহেলী সভ্যতার কোন প্রভাবই কবুল করিবেন না। সেই সঙ্গে তাঁহাদের যাবতীয় ধন-সম্পদের একটি পূর্ণ তালিকাও তৈয়ার করিয়া লইতেন; উত্তরকালে কাহারো ধন-সম্পদে অস্বাভাবিক স্ফীতি পরিলক্ষিত হইলে পূর্বাহ্ণে রচিত তালিকার সহিত উহার তুলনা ও যাচাই করিয়া দেখিতেন। কাহারো সম্পত্তি অকারণে স্ফীত হইতে দেখিলে তাহার অর্ধেক পরিমাণ বায়তুলমালে ক্রোক করিয়া লইতেন।
শাসক ও পদস্থ অফিসারগণ যাহাতে কোথাও সীমানা লঙ্ঘন করিতে না পারে, সেদিকে খলীফা উমর (রা)-এর বিশেষ দৃষ্টি ছিল। এইজন্য তিনি প্রত্যেক হজ্জের সময়ই সাধারণভাবে ঘোষণা করিয়া দিতেন, কোন সরকারী কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কাহারো কোন অভিযোগ থাকিলে তাহা অনিতিবিলম্বে খলীফার গোচরীভূত করিতে হইবে। সেই সঙ্গে তিনি সকল অভিযোগের যথোচিত প্রতিকারেরও সুষ্ঠু ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন, যেন কোন অভিযোগ শুধু অভিযোগের পর্যায়েই থাকিয়া না যায়, বরং প্রতিটিরই যেন আশু প্রতিকার গ্রহণ করা হয়।
শাসকদের দ্বার জনগণের জন্য সর্বদা উন্মুক্ত রাখার জন্য খলীফাতুল মুসলিমীন বিশেষ তাকিদ করিতেন। জনগণের ফরিয়াদ শাসকদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করার পথে কোথাও বিন্দুমাত্র বাঁধার সৃষ্টি হইতে দেখিলে তিনি অবলিম্বে তাহা দূরীভূত করিয়া দিতেন। তিনি দায়িত্বশীল সরকারী কর্মচারীদিগকে দৈনন্দিন কর্তব্য পালনে সদা তৎপর থাকার জন্য সব সময় তাকীদ করিতে থাকিতেন। এই পর্যায়ে হযরত আবূ মূসা আশয়ারী(রা) কে যে উপদেশ পাঠাইয়াছিলেন, তাহা সর্বকালের সর্বদেশের সরকারী কর্মচারীদের জন্য মহামূল্য দিক-নির্দেশনারূপে গণ্য হইবে। তিনি লিখিয়াছিলেনঃ
*******(আরবী)
অতঃপর জানিবে, সুষ্ঠু কর্মপন্থা এই যে, অদ্যকার কাজ আগামী কালের জন্য ফেলিয়া রাখিবে না। এইরূপ করিলে তোমাদের নিকট অনেক কাজ জমিয়া যাইবে। ফলে কাজের চাপে তুমি দিশাহারা হইয়া পড়িবে। কি করিবে, কোনটা করিবে, কোনটা করিবে না, তাহার দিশা পাইবে না। পরিনামে সব কাজই বিনষ্ট করিয়া ফেলিবে।
জনগণের নৈতিক মান সংরক্ষণ
শাসকদের ছাড়াও ইসলামী রাষ্ট্রের অধিবাসী সাধারণ জনগণের নৈতিক চরিত্র ও ধর্মীয় মর্যাদা সংরক্ষণের জন্য খলীফা বিশেষ দায়িত্ব সহকারে অবিরাম কাজ করিতেন। বস্তুত তিনি নিজে যেরূপ ইসলামী নৈতিকতার বাস্তব প্রতীক ছিলেন, সমষ্টিগতভাবে গোটা মুসলিম জাতিকে এবং ব্যক্তিগতভাবে প্রতিটি মুসলিমকে অনুরূপ গড়িয়া তোলার জন্য তিনি আপ্রাণ চালাইয়া যাইতেন। তৎকালে বংশীয় আভিজাত্যের ঐতিহিক গৌরব এবং ব্যক্তিগত অহংকার আরবদের হাড়ে-মজ্জায় মিশ্রিত ছিল, মনীব ও নওকরের মাঝে ছিল মানুষ-অমানুষের পার্থক্য। কিন্তু দ্বিতীয় খলীফা ইসলামী শিক্ষা ও নৈতিক ভাবধারার গতি-প্রবাহে এইসবের কলংক ও আবর্জনারাশি ধুইয়া-মুছিয়া নিঃশেষ করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি নিজে খাদ্য গ্রহণকালে ফকীর-মিসকিন ও ক্রীতদাসদের নিজের সঙ্গে বসাইয়া খাওইতেন। তিনি বলিয়াছেনঃ ‘ক্রীতদাস ও ফকীর-মিসকীনের সঙ্গে একত্রে আহার করাকে যাহারা লজ্জাকর ও মর্যাদাহানিকর মনে করে, তাহাদের উপর আল্লাহ্র অভিশাপ’। বস্তুত দুনিয়ার ইতিহাসে আজ পর্যন্ত এইরূপ সাম্যবাদী শাসকের অন্য কোন দৃষ্টান্ত খুঁজিয়া পাওয়া যাইতে পারে না।
তৎকালীন সমাজের লোকদের উপর কবি ও কবিতার খুব প্রভাব ছিল। যেসব কবি লোকদের প্রতি অশ্লীল গালাগালমূলক কবিতা রচনা করিত, রাষ্ট্রীয় ফরমান প্রচার করিয়া খলীফা উমর (রা) সেসব বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন।লোকদের পরস্পরের মধ্যে হিংসা ও বিদ্বেষাগ্নি দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া মুসলিম ভ্রাতৃত্বের সুদৃঢ় প্রাসাদকে যাহাতে ভস্ম করিয়া দিতে না পারে এবং জনসাধারণ যাহাতে জাতীয় লক্ষ্য ও আদর্শ ভুলিয়া গিয়া আয়েশ-আরাম, জাঁকজমক, বিলাসিতা ও ভোগ-সম্ভোগে লিপ্ত হইয়া না পড়ে, সেদিকে তাঁহার বিশেষ নজর ছিল।
মোটকথা, মুসলমানদিগকে সকল প্রকার নৈতিক পতনের হাত হইতে রক্ষা করিয়া তাহাদিগকে উন্নত নৈতিক চরিত্রে ভূষিত করার জন্য তিনি বিশেষ যত্ন গ্রহন করিয়াছিলেন। সমাজের লোকদের মধ্যে পরিপূর্ণ সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব স্থাপন, তাহাদের মধ্যে আত্মসম্মানবোধ ও দায়িত্বজ্ঞান জাগ্রত করার জন্য তিনি কখনো চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। প্রাদেশিক শাসনকর্তাদিগকেও এ সম্পর্কে সর্বদা সতর্ক করিয়া রাখিতে চেষ্টা করিতেন।
আভ্যন্তরীণ শাসন-শৃঙ্খলা ব্যবস্থা
সিরিয়া ও ইরান দখলে আসার পর পর বিজিত অঞ্চলের কৃষি-জমি বিজয়ী সেনানীদের মধ্যে বণ্টন করার দাবি উঠিলে খলীফা তাহা অস্বীকার করেন। মজলিসে শুরার অধিবেশনে বিস্তারিত আলোচনার পর উমর ফারুক (রা)-এর মতের অনুকূলেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।
ফারুকী খিলাফতের আমলেই ইরাকের বিরাট এলাকার জরিপ গ্রহণ করা হয় সেখানকার চাষোপযোগী সমস্ত জমি জনসাধারণের মধ্যে বণ্টন করা হয়। তাহাদের নিকট হইতে উশর ও খারাজ আদায়ের ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। সিরিয়া ও মিসরে রাজস্ব আদায় শুরু করা হয়। ব্যবসায় শুল্ক(duty tax) আদায় করা খলীফা উমর ফারুক (রা)-এর একটি ইজতিহাদী ফয়সালা এবং ইসলামী রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় তাঁহার আমলেই সর্বপ্রথম ইহার সূচনা হয়। বলাবাহুল্য, ইহা ইসলামের অর্থ-বিজ্ঞানের সহিত পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল।
দ্বিতীয় খলীফা সমগ্র মুসলিম জাহানের আদমশুমারী গ্রহণ করেন। তাঁহার আমলে জিলাসমূহে রীতিমত আদালত ও ফৌজদারী কোর্ট স্থাপিত হয়। বিচার বিভাগের জন্য প্রয়োজনীয় নিয়ম-কানুন নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়। বিচারকদের জন্য উচ্চহারে বেতন নির্ধারণ করা হয়, যেন ঘুষ-রিসওয়াতের প্রশ্রয় দেওয়ার বিন্দুমাত্র কারণ না ঘটে। ইহা ছাড়া বিভিন্ন জটিল বিষয়ের মীমাংসার জন্য তখন ফতোয়া বিভাগও খোলা হয়।
দেশের আভ্যন্তরীণ শান্তি ও নিরাপত্তা বিধানের জন্য তিনি পুলিশ বিভাগ স্থাপন করেন। হযরত আবূ বকর (রা)-কে বাহরাইনের সর্বোচ্চ পুলিশ কর্মচারী নিযুক্ত করিয়া পাঠাইবার সময় তাঁহাকে শান্তি ও নিরাপত্তা বিধানের সঙ্গে সঙ্গে জনগণের নৈতিক চরিত্রের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখার জন্য তিনি বিশেষ নির্দেশ দিয়াছিলেন। দোকানদারগণ যেন পরিমাপ ও ওজনের দিক দিয়া ক্রেতাকে বিন্দুমাত্র ঠকাইতে না পারে, রাজপথের উপর যেন কেহ ঘর-বাড়ি নির্মাণ না করে, ভারবাহী জন্তুর উপর দুর্বহ কোন বোঝা যেন চাপানো না হয় এবং শরাব উৎপাদন ও ক্রয়-বিক্রয় হইতে না পারে, সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবার জন্য পুলিশ বাহিনীকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। বস্তুত জনস্বার্থ ও শরীয়াতের নির্দেশ যাহাতে কিছুমাত্র ব্যাহত হইতে না পারে, বরং উভয়েরই মর্যাদা পুরাপুরি রক্ষা পাইতে পারে সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখাই ছিল পুলিশের মৌলিক দায়িত্ব।
ফারুকে আযম (রা)-এর পূর্বে আরব জাহানে কারাগারের কোন অস্তিত্ব ছিল না। তিনিই প্রথমবার মক্কা শরীফে কারাগার স্থাপন করেন। উত্তরকালে জিলাসমূহে কেন্দ্র-স্থলেও অনুরূপ কারাগার স্থাপন করা হয়।
বায়তুলমাল প্রতিষ্ঠা
ফারুকী খিলাফতের পূর্বে সরকারী ধন-সম্পদ সঞ্চিত রাখার কোন স্থায়ী প্রতিষ্ঠান বর্তমান ছিল না। যাহাকিছুই আমদানী হইত, সঙ্গে সঙ্গে তাহা প্রয়োজনীয় কাজে কিংবা অভাবগ্রস্তদের সাহায্যার্থে ব্যয় হইয়া যাইত। হযরত আবূ বকর (রা) যদিও একখানি ঘর বায়তুলমাল কায়েমের জন্য নির্দিষ্ট করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহা প্রায় সবসময় বন্ধ থাকিত; তাহাতে সঞ্চয় করিয়া রাখার মত কোন সম্পদই তখন ছিল না। তাঁহার ইন্তেকালের সময় বায়তুলমালে তল্লাসী চালানো হইতে উহাতে একটি মাত্র মুদ্রা অবশিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। হযরত উমর (রা) সম্ভবতঃ ১৫হিজরী সনে সর্বপ্রথম বায়তুলমাল প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন ও মজলিসে শু’রার মঞ্জুরীক্রমে মদীনা শরীফে বিরাটাকারে বায়তুলমাল প্রাসাদ নির্মাণ করেন। রাজধানীতে বায়তুলমাল প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর জিলা কেন্দ্রসমূহেও অনুরূপ বায়তুলমাল প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রতিটি স্থানেই এই বিভাগের জন্য সতন্ত্র অফিসার নিযুক্ত করা হয়। শাখা বায়তুলমালসমূহের বার্ষিক আয় হইতে স্থানীয় খরচ নির্বাহ করার পর যাহাকিছু উদ্ধৃত্ত থাকিত, তাহা কেন্দ্রিয় বায়তুলমালে-মদীনা তাইয়্যেবায়-প্রেরণ করা হইত। বায়তুলমালের দায়িত্ব ও ব্যয়ভার সম্পর্কে সঠিক অনুমান করার জন্য এই কয়টি কথাই যথেষ্ট যে, রাজধানীর অধিবাসীদের জন্য যে বেতন ও বৃত্তি নির্দিষ্ট ছিল, তাহার পরিমাণই ছিল তিন কোটি দিরহাম। বায়তুলমালের হিসাব রক্ষার জন্য সতন্ত্র বিভাগ ও হিসাবের বিভিন্ন জরুরী খাতাপত্রও যথাযথভাবে চালু করা হইয়াছিল। আরবে তখনো সুষ্ঠুভাবে কোন বৎসর গণনা প্রচলিত ছিল না; হযরত উমর ফারুক (রা) ১৬ হিজরীতে হিজরী সনের হিসাব চালু করিয়া এই অভাব পূরন করিয়া দেন।
গৃহ নির্মাণ ও পূর্তবিভাগীয় কাজ
ইসলামী রাষ্ট্রের পরিধি যতই বিশাল আকার ধারণ করিতে থাকে, বিভিন্ন দালান-কোঠা নির্মাণের কাজ ততই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। হযরত উমর (রা)-এর শাসনামলে এই কার্য সম্পাদনের জন্য স্বতন্ত্র কোন বিভাগ ছিল না। তাহা সত্ত্বেও প্রাদেশিক শাসনকর্তা ও উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের দায়িত্বে এই কাজ সুষ্ঠুরূপে অগ্রসর হইতে থাকে। প্রতিটি স্থানেই অফিসারদের বসবাসের জন্য সরকারী দালান-কোঠা ও জনগণের সুখ-সুবিধার জন্য পুল, সড়ক ও মসজিদ নির্মিত হয়। অনুরূপভাবে সামরিক প্রয়োজনে দুর্গ, ক্যাম্প ও বারাকসমূহ নির্মাণ করা হয় এবং রাজকোষের হেফাজতের জন্য বায়তুলমাল বা খাজাঞ্জীখানার দালান তৈয়ার করা হয়। রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে হযরত উমর (রা)-এর ব্যয়-সংকোচন নীতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাহা সত্ত্বেও বায়তুলমালের প্রাসাদ সাধারণতঃ বেশী মজবুত ও জাঁকালভাবে তৈয়ার করা হয়।
মক্কা ও মদীনার মধ্যে বিশেষ সম্পর্কের কারণে উভয় শহরের যোগাযোগ ও যাতায়াত ব্যবস্থা অত্যন্ত সুগম ও শান্তিপূর্ণ হওয়া আবশ্যক ছিল। হযরত উমর (রা) মদীনা হইতে মক্কা পর্যন্ত দীর্ঘ পথের পার্শ্বে অনেকগুলি পুলিশী পাহারা, সরাইখানা ও ঝর্ণাধারা নির্মাণ করেন।
কৃষিব্যবস্থার উন্নয়ন ও উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য খলীফা সমগ্র দেশে কূপ বা খাল খনন করিয়া সেচকার্য সম্পাদনের সুষ্ঠু ব্যবস্থা করিয়া দেন। বসরায় মিষ্টি পানি সরবরাহের উদ্দেশ্যে দজলা নদী হইতে খাল খনন করা হয়। এই খালের দৈর্ঘ্য ছিল প্রায় নয় মাইল।এই প্রসঙ্গে নহরে মা’কাল, নহরে মায়াদ ও নহরে আমীরুল মু’মিনীন-এর কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।
শহর নির্মাণ
আরবের উষর-ধূষ্র মরুভূমির বুক হইতে বিশ্ব-বিজয়ী শক্তি হিসাবে মুসলিমগণ যখন বহির্বিশ্বে পদার্পণ করিল, তখন অন্যান্য দেশের সবুজ-শ্যামল ও মনোরম দৃশ্য তাহাদিগকে মুগ্ধ করে। ইসলামী আদর্শ প্রচার ও প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব পালনের জন্য ইসলামী রাষ্ট্রের তরফ হইতে বিভিন্ন সরকারী কার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে তাহারা রাজধানী মদীনা হইতে বহু দূর দূরাঞ্চলে বসবাস অবলম্বন করিতে বাধ্য হয়। ইহার ফলে তাহাদের দ্বারা প্রতিবেশী দেশসমূহ বিভিন্ন শহর ও নগর গড়িয়া উঠে। হযরত উমর ফারুক (রা)-এর খিলাফত কালে বসরা,কুফা, ফুস্তাত, মুসেল প্রভৃতি ইতিহাস-বিখ্যাত নগরসমূহ স্থাপিত হয়। বসরা শহরে প্রথমে মাত্র আটশত লোক বসবাস শুরু করে; পরে অল্পদিনের মধ্যেই অধিবাসীদের সংখ্যা প্রায় এক লক্ষ বিশ হাজার পর্যন্ত পৌঁছে। ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্র হিসাবে এই শহর শতাব্দী কাল পর্যন্ত মুসলমানদের গৌরবের বস্তু হইয়া থাকে। ইরাকের জৈনক আরব শাসনকর্তা রাজধানী পুনঃনির্মাণ করায় কুফা নগরের সৃষ্টি হয়। এই শহরে চল্লিশ হাজার লোকের বাসোপযোগী গৃহাদি নির্মাণ করা হয়। হযরত উমর (রা)-এর নির্দেশক্রমে ইহার সড়কসমূহ চল্লিশ হাত প্রশস্ত করিয়া তৈয়ার করা হয়। এখানে যে জামে মসজিদ নির্মিত হয়, তাহাতে এক সঙ্গে চল্লিশ হাজার মুসলমান নামায আদায় করিতে পারে। জ্ঞান-বিজ্ঞান-কেন্দ্র হিসাবে এই শহরের ঐতিহাসিক মর্যাদা সর্বজনবিদিত।
ফুস্তাত শহর নির্মাণের ইতিহাস অত্যন্ত মর্মস্পর্শী। মিসর বিজয়ী হযরত আমর ইবনুল আস (রা) নীল দরিয়া ও মাকতাম পর্বতের মধ্যবর্তী স্থানে সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করেন। এই সময় ঘটনাবশতঃএকটি কবুতর তাঁহার তাঁবুতে নীড় রচনা করে। হযরত আমর (রা) যখন এই স্থান ত্যাগ করিয়া যাইতেছিলেন, তখন এই আসমানী অতিথির শান্ত-নীড় জীবনে যেন কোনরূপ ব্যাঘাত সৃষ্টি না হয় সেই চিন্তায় তিনি তাঁবুকে যথাযথভাবে দাঁড় করিয়া রাখিলেন। উত্তরকালে এই তাঁবুকে কেন্দ্র করিয়াই ফুস্তাত শহর গড়িয়া উঠে। চতুর্থ শতাব্দীর জৈনক পর্যটক এই শহর সম্পর্কে লিখিয়াছেনঃ
এই শহর বাগদাদের প্রতিদ্বন্দ্বী পাশ্চাত্যের কেন্দ্র ও ইসলামের গৌরব। এখানকার জামে মসজিদ অপেক্ষা মুসলিম জাহানের আর কোন মসজিদে জ্ঞান-বিজ্ঞান আলোচনার এতো বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় না। এখানকার সামুদ্রিক বন্দরে দুনিয়ার অধিক সংখ্যক জাহাজ নোঙর করিয়া থাকে।
মুসেল শহর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যর সংগমস্থলে অবস্থিত; এই দৃষ্টিতেই সম্পূর্ণ গ্রামীণ পরিবেশে নির্মিত এই শহরের নামকরণ হইয়াছে। ইহা একটি অজ পাড়াগাঁকে বিরাট শহরে পরিণত করার এক বাস্তব নিদর্শন। হযরত উমর (রা)-এর নির্দেশে এখানে একটি বিশাল জামে মসজিদ নির্মাণ করা হয়। আলেকজান্দ্রিয়া বিজয়ের পর হযরত আমর ইবনুল আস(রা) সমুদ্রোপকূলে কিছু সংখ্যক সৈন্য রাখিয়া দেন। কেননা সমুদ্র-পথে রোমান শত্রুদের আক্রমণের ভয় ছিল। উত্তরকালে এখানে একটি বিরাট উপনিবেশ গড়িয়া উঠে।
সামরিক ব্যবস্থাপনা
ইসলাম যখন রোমান সাম্রাজ্য অপেক্ষাও অধিক বিশাল রাজ্যের মালিক হইয়া বসিল এবং কাইসার ও কিসরার বিশাল বিস্তীর্ণ রাজ্যসমূহ উহার অধিকারভুক্ত হইল, তখন একটি সুসংবদ্ধ সামরিক ব্যবস্থাপনা উহার জন্য অপরিহার্য হইয়া পড়ে। হযরত উমর (রা) ১৫ হিজরী সনে ে সম্পর্কে কার্যকর নীতি অবলম্বন করেন এবং সমগ্র মুসলিম জাহানকে সামরিক জাতি রূপে গড়িয়া তোলার চেষ্টা শুরু করে। প্রথম পর্যায়ে আনসার ও মুহাজির মুসলমানদিগকে লইয়া কাজ আরম্ভ করা হয়। তাহাদের প্রত্যেকের জন্য মর্যাদানুপাতে বেতন ধার্য করা হয়। এই ব্যাপারে বিশেষ লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, যাহাদের জন্য যত পরিমাণ বেতন ধার্য করা হয়, তাহাদের ক্রীতদাসদের জন্যও সম পরিমাণ বৃত্তি নির্দিষ্ট করা হয়।
কিছুদিন পর এই নীতি আরো অধিক ব্যাপক আকারে ধারণ করে। আরবের সমগ্র গোত্র ও কবীলার লোকদিগকেও ইহার অন্তর্ভুক্ত করিয়া লওয়া হয়। শেষ পর্যন্ত দুগ্ধপোষ্য শিশুদের জন্যও বৃত্তি নির্ধারণ করা হয়। ইহার অর্থ এই ছিল যে, আরবের জাহানের প্রতিটি শিশুকে জন্মদিন হইতেই ইসলামী সৈন্যবাহিনীর একজন সিপাহীরুপে গণ্য করা হইল।
সৈনিকদিগকে বিশেষভাবে ট্রেনিং দানের দিকে হযরত উমর (রা)-এর সতর্ক দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল; এমনকি বিজিত এলাকাসমূহের কেহ যেন সামরিক জীবন পরিত্যাগ করিয়া কৃষিকার্য ও ব্যবসায়-বাণিজ্যে লিপ্ত হইয়া না পড়ে, সে জন্য বিশেষ তাকীদী ফরমান প্রচার করা হইয়াছিল। কেননা তাহা করা হইলে মুসলিম মুজাহিদদের সামরিক যোগ্যতা প্রতিভা, বীরত্ব ও সাহসিকতা বিলুপ্ত হইয়া যাওয়ার সমূহ আশংকা ছিল।
দ্বিতীয় খলীফার আমলে সৈনিকদের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য বিশেষ যত্ন লওয়া হইত; সৈনিকদের ক্যাম্প তৈয়ার করার ব্যাপারে আবহাওয়ার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা হইত। বসন্তকালে সৈনিকদের সবুজ-শ্যামল অঞ্চলে প্রেরণ করা হইত। প্রায় সকল বড় বড় শহরের উপকণ্ঠে সামরিক কেন্দ্র স্থাপন করা হইয়াছিল। শত্রু শিবির হইতে গোপন সংবাদ সংগ্রহের জন্য সামরিক গোয়েন্দা বিভাগকে বিশেষ তৎপর করিয়া তোলা হইয়াছিল। বস্তুতঃহযরত উমর ফারুক (রা) তেরোশত বৎসর পূর্বে যে সামরিক রীতি-নীতি নির্ধারণ করিয়াছিলেন, মূল-নীতির দিক দিয়া প্রায় দেড় হাজার বৎসর পরও তাহাতে কিছুমাত্র রদ-বদল হওয়াতো দূরের কথা, তাহাতে কিছু পরিবর্ধন করাও আজ পর্যন্ত সম্ভব হয় নাই। আরবদের শানিত তরবারি বিজয় লাভের ব্যাপারে কখনো অপর কাহারো অনুগ্রহভাজন হইতে প্রস্তুত হয় নাই; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও শত্রুপক্ষকে তাহাদেরই স্বগোত্রীয় জাতিসমূহের সহিত সংগ্রামে লিপ্ত করিয়া দেওয়া সমর কৌশলের একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি বলিয়া হযরত উমর (রা) বিশেষ কৃতিত্ব সহকারেই এই রণকৌশল কার্যকর করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ফলে অনারব, রোমান ও গ্রীক জাতির অসংখ্য বীর-যোদ্ধা ইসলামী সৈন্যবাহিনীতে শামিল হইয়া নিজ নিজ জাতির লোকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছেন, ইতিহাসে ইহা চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিব।
ইসলামের প্রচারের কাজ
হযরত উমর ফারুক (রা) ধর্ম-প্রচার ও প্রতিষ্ঠার কাজ বিশেষ মনোযোগ সহকারেই সম্পন্ন করিতেন। লোকদিগকে ইসলামে দীক্ষিত করার ব্যাপারে তিনি কখনো তরবারি কিংবা রাষ্ট্র-শক্তি প্রয়োগ করেন নাই; বরং ইসলামী জীবনাদর্শের বৈশিষ্ট্য, ইহার অতুলনীয় সৌন্দর্য এবং অন্তর্নিহিত মর্মস্পর্শী ভাবধারায় মুগ্ধ ও আকৃষ্ট করিয়াই তিনি লোকদিগকে মুসলিম বানাইতে চেষ্টা করিতেন। তিনি তাঁহার ক্রীতদাসকে ইসলাম কবুল করার আহ্বান জানাইলে উহা গ্রহণ করিতে সে স্পষ্ট ভাষায় অস্বীকার করে। তখন তিনি বলিলেন ‘লা-ইকরাহা ফিদ্বীন’- ‘দ্বীন ইসলাম কবুল করার ব্যাপারে কোন জোর-জবরদস্তি করা যাইতে পারে না’।
কাফিরের সহিত সংগ্রাম ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া শেষবারের তরে ও সর্বশেষ সুযোগ হিসাবে তিনি ইসলাম কবুল করার দাওয়াত পেশ করিয়াছেন। কেননা ঠিক সেই মুহূর্তেও কেহ ইসলাম কবুল করিলে তাদের সহিত যুদ্ধ করা হারাম হইয়া যায়। যুদ্ধ ও রক্তপাত পরিহার করার জন্য ইহা ছিল মুসলমানদের শেষ প্রচেষ্টা। হযরত উমর (রা) সমগ্র মুসলমানকে ইসলামী নৈতিকতার জীবন্ত প্রতীকরূপে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। ফলে যে পথ ও জনপদের উপর হইতেই তাহারা অগ্রসর হইত, সেখানেই তাহাদের নৈতিক-চরিত্র ও মধুর ব্যবহারের প্রভাব প্রতিফলিত হইত এবং সত্য-সন্ধ জনতা তাহাতে মুগ্ধ ও বিমোহিত হইয়া ইসলামে দীক্ষিত হইত। রোমান সম্রাটের রাষ্ট্রদূত ইসলামী সৈন্য-কেন্দ্রে আগমন করিলে সেনাপতির সরল জীবন-যাত্রা, অকপটতা ও উদার ব্যবহার দেখিতে পাইয়া স্বতঃস্ফূর্তভাবে ইসলাম গ্রহণ করেন। মিসরের জনৈক প্রভাশালী ব্যক্তি মুসলমানদের বৈশিষ্ট্যের সাথে লোকমুখে শুনিতে পাইয়া এতদূর মুগ্ধ হন যে, দুই সহস্র জনতাসহ অনতিবিলম্বে ইসলাম কবুল করেন।
ইসলাম প্রচারের পর সর্বাপেক্ষা জরুরী কাজ ছিল স্বয়ং মুসলমানদিগকে ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া তোলা ও ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতির বাস্তব প্রতিষ্ঠা করা। এই পর্যায়ে হযরত উমর (রা)-এর প্রচেষ্টা প্রথম খলীফার আমল হইতেই বিশেষভাবে শুরু হইয়াছিল। ইসলামের উৎস ও একমাত্র মূলসূত্র কুরআন মজীদ গ্রন্থাকারে প্রকাশ করার মূলে উমর ফারুক (রা)-এর প্রচেষ্টা সর্বজনবিদিত। খলীফা হইয়া তিনি পূর্ণ শক্তিতে উহার ব্যাপক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন। এই উদ্দেশ্যে নিযুক্ত শিক্ষকদিগের জন্য সম্মানজনক বেতন নির্ধারণ করা হয়। সিরিয়ার কয়েকজন বিশিষ্ট সাহাবিকে কুরআন শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হয়। কুরআন মজীদকে পূর্ণ বিশুদ্ধ ও নির্ভুলরূপে অধ্যয়ন করার জন্য চতুর্দিকে ব্যাপকভাবে কুরআন চর্চা শুরু হইয়া যায়।
ইসলামী জীবন-ব্যবস্থায় কুরআনের পরই হইতেছে হাদীসের স্থান। হাদীসের খেদমত করার ব্যাপারেও হযরত উমর ফারুক (রা)-এর আন্তরিক প্রচেষ্টার অন্ত ছিল না। তিনি নবী করীম (স)-এর বহু সংখ্যক হাদীস লিপিবদ্ধ করিয়া প্রদেশসমূহের শাসনকর্তাদের নামে পাঠাইয়াছিলেন এবং সাধারণ্যে তাহা প্রচার করার নির্দেশ দিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া বিভিন্ন সাহাবীকে হাদীস শিক্ষাদানের জন্য কুফা,বসরা ও সিরিয়া প্রভৃতি এলাকায় তিনি প্রেরণ করিয়াছিলেন।
হযরত উমর ফারুক (রা) অবশ্য হাদীস গ্রহণের ব্যাপারে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতেন। কেননা মুহাদ্দিসদের দৃষ্টিতে সকল সাহাবীই বিশস্ত ও নির্ভরযোগ্য হইলেও তাঁহারা কেহই মানবীয় বৈশিষ্ট্য ও গুনাগুণের ঊর্ধ্বে ছিলেন না, একথা তিনি খুব ভালো করিয়া জানিতেন। এই কারণে তিনি বেশী পরিমাণে হাদীস বর্ণনা করা সম্পর্কে লোকদিগকে বিশেষভাবে সতর্ক করিয়া দেন এবং লোকেরা যাহাতে প্রথমেই কুরআনের দিকে লক্ষ্য আরোপ করে এবং ইহার পর হাদীস গ্রহন করে, সেজন্য তিনি সংশ্লিষ্ট সকলকেই সতর্ক করিয়া দেন।
হাদীসের পরই হইতেছে ফিকাহর স্থান। খলীফা উমর (রা) নিজেই বিভিন্ন খোতবা প্রসঙ্গে ফিকাহর মসলা-মাসায়েল বর্ণনা করিতেন এবং দূরবর্তী স্থানের শাসকদের নামেও ফিকাহর জরুরী মুসলাসমূহ সময় সময় লিখিয়া পাঠাইতেন। যে সব বিষয়ে মতবৈষম্যের সৃষ্টি হইত, তাহা সাহাবীদের প্রকাশ্য মজলিসে তিনি পেশ করিতেন ও যথাসম্ভব সর্বসম্মতভাবে মিমাংসা করিয়া লইতেন। জিলার পদস্থ কর্মচারী নিয়োগের ব্যাপারে লোকদের ইসলামী বিধান ও আইন-কানুন সম্পর্কিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার দিকে তিনি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতেন এবং সমগ্র মুসলিম জাহানে ইসলামী আইনের ব্যাপক প্রচারের জন্য ফিকাহবিদগণকে উচ্চমানের বেতনে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সংক্ষেপ কথা এই যে, দ্বিতীয় খলীফার শাসন আমলে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের ব্যাপক শিক্ষা ও প্রচারের সুষ্ঠু ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। দ্বিতীয় খলীফার আমলে সমগ্র এলাকায় মসজিদ নির্মাণ এবং তাহাতে ইমাম মুহাযযিন নিযুক্ত করা হয়। লোকদের সুবিধার্থে হেরেম শরীফ অধিক প্রশস্ত করিয়া দেওয়া হয়। মসজিদে নববীকেও অনেক বড় করিয়া তৈয়ার করা হয়। তিনি প্রত্যেক বৎসরই নিজে হজ্জে গমন করিতেন ও হাজীদের যাবতীয় সুখ-সুবিধা বিধানের দিকে নিজেই লক্ষ্য রাখিতেন।
সাধারণ জনকল্যাণমূলক কাজ
১৮ হিজরীতে আরবদেশে যখন সর্বগ্রাসী দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, তখন হযরত উমর (রা) গভীরভাবে উদ্বিগ্ন,সন্ত্রস্ত ও বিচলিত হইয়া পড়েন। তিনি নিজে এই সময় সকল প্রকার সুখ-সম্ভোগ, আরাম-আয়েশ ও চর্ব্য-চোষ্য-লেহ্য পেয়র স্বাদ আস্বাদন পরিহার করেন। তাঁহার নিজের পুত্রকে ফল খাইতে দেখিয়া খলীফা ক্রুদ্ধঃহইয়া বলিলেনঃ ‘সমগ্র দেশবাসী বুভুক্ষু, ক্ষুধার যন্ত্রণায় ছটফট করিতেছে আর তুমি সুমিষ্ট ও পুষ্টিকর ফলের স্বাদ গ্রহন করিতেছ? এই সময় জনগণের দুঃখ-কষ্ট লাঘব করার জন্য তিনি যে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন,ইতিহাসে তাহা চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। এই সময় বায়তুলমালের সমস্ত ধন-সম্পদ তিনি অকুণ্ঠিত চিত্তে ব্যয় করেন এবং চারিদকে হইতে খাদ্য আমদানী করিয়া দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িতদের মধ্যে বণ্টন করেন। তিনি লা-ওয়ারিস শিশুদিগকে দুগ্ধ-পান ও লালন-পালন করার সুষ্ঠু ব্যবস্থা করেন এবং গরীব-মিসকীনদের জন্য জীবিকার সংস্থান করেন। তবে তাহার এই ব্যবস্থা সাধারণভাবে সকল গরীব ও মিসকীনদের জন্য ছিল না, বিশেষভাবে যাহারা উপার্জনে অক্ষম ছিল, তাহাদের জন্যই ছিল এই ব্যবস্থা।
হযরত উমর (রা)-এর আশ্চার্যজনক কর্মনীতি এই ছিলে যে, তিনি আঙ্গুর ফসলের উপর অতিরিক্ত কর ধার্য করিতেন এই জন্য যে, তাহা ছিল তখনকার যুগে একমাত্র ধনীদের খাদ্য আর খেজুরের উপর অপেক্ষাকৃত কম কর ধার্য করিতেন; কেননা তাহা ছিল অপেক্ষাকৃত গরীব ও সাধারণ জনগণের খাদ্য।
দেশের দূরবর্তী এলাকাসমূহের আভ্যন্তরীণ খুঁটিনাটি অবস্থা সম্পর্কেও হযরত উমর (রা) বিশেষভাবে অবহিত থাকিতেন এবং কোন কিছুই তাঁহার অজ্ঞাত ও দৃষ্টির অগোচর থাকিতে পারিত না। এমন কি, লোকদের পারিবারিক জীবনের বদ্ধ পরিবেশেও কোন প্রকার শরিয়াত-বিরোধী অনাচারের সৃষ্টি হইলে অথবা কেহ অভাব-দারিদ্রের নিষ্ঠুর আঘাতে জর্জরিত হইয়া থাকিলে তাহাও খলীফা উমর ফারুক (রা)-এর অজ্ঞাত থাকিয়া যাইত না। এইজন্য তিনি সমগ্র দেশে রিপোর্টার ও বিবরণকারী লোক নিযুক্ত করেন। ঐতিহাসিক তাবারী লিখিয়াছেনঃ
******(আরবী)
উমর ফারুক (রা) কোন বিষয়েই অনবহিত থাকিতেন না। ইরাকে যাহারা বিদ্রোহ করিয়াছিল এবং সিরিয়ায় যাহাদিগকে পুরস্কৃত করা হইয়াছিল, সেইসব কিছুর বিস্তৃত বিবরণ তাঁহাকে লিখিয়া পাঠান হইয়াছিল।
হযরত উমর (রা)-এর গোয়েন্দা বিভাগ এক শাসনকর্তা গোপন বিলাস জীবনের বিবরণ তাহার এক পত্রের মাধ্যমে জানিতে পারে। খলীফা এই বিষয়ে অবহিত হইয়া তাহাকে পদচ্যুত করেন এবং লেখেন যে, তোমার বর্তমান জীবন ধারণ আমি সহ্য করিতে পারি না।
বিচার ইনসাফ
ফারুকী খিলাফতের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য দিক তাঁহার নিরপেক্ষ, সুবিচার ও পক্ষপাতহীন ইনসাফ। তাঁহার শাসন আমলে এক বিন্দু পরিমাণ না-ইনসাফীও অনুষ্ঠিত হইতে পারিত না।
ফারুকে আযম (রা)-এর এই ঐতিহাসিক বিচার-ইনসাফ কেবল মুসলমান পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিল না, তাঁহার সুবিচারের দ্বার ইয়াহুদী,খৃস্টান,মাজুসী প্রভৃতি অমুসলিম নাগরিকদের জন্যও অবারিত ও চির-উন্মুক্ত ছিল। হযরত উমর (রা) জনৈক অমুসলিম বৃদ্ধ ব্যক্তিকে ভিক্ষা করিতে দেখিয়া ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে উত্তরে সে বলিলঃ ‘আমার উপর ‘জিজিয়া’ ধার্য করা হইয়াছে, অথচ আমি একজন গরীব মানুষ’। হযরত উমর (রা) তাহাকে নিজের ঘরে লইয়া গেলেন ও কিছু নগদ সাহায্য করিলেন এবং বায়তুলমালের ভারপ্রাপ্তকে লিখিলেনঃ ‘এই ধরণের আরও যত ‘যিম্মী’ গরীব লোক রহিয়াছে, তাহাদের সকলের জন্য বৃত্তি নির্দিষ্ট করিয়া দাও। আল্লাহ্র কসম, ইহাদের যৌবনকাল কাজ আদায় করিয়া বার্ধক্যে ইহাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা না করা কিছুতেই ইনসাফ হইতে পারে না’। বস্তুত দুনিয়ার মানুষের দুঃখ মোচনের জন্য উমর ফারুক (রা)-এর খিলাফত চিরদিনের জন্য এক উজ্জ্বল আদর্শ।
হযরত উসমান (রা)- এর চরিত্র বৈশিষ্ট্য
হযরত উসমান (রা) খিলাফতে রাশেদা’র তৃতীয় খলীফা। তাঁহার ব্যক্তিগত চরিত্রে ‘খলীফায়ে রাশেদ’ হওয়ার সব বৈশিষ্ট্যই পূর্ণ মাত্রায় বর্তমান ছিল। তিনি স্বভাবতঃই পবিত্রচরিত্র,বিশ্বাসপরায়ণ,সত্যবাদী, ন্যায়নিষ্ঠ, সহনশীল এবং দরিদ্র-সহায় ছিলেন। জাহিলিয়াহ যুগের ঘোরতর মদ্যপায়ী সমাজে বসবাস করা সত্ত্বেও মদ্য ছিল তাঁহার অনাস্বাদিত। রাসূলে করীম (স)-এর পবিত্র সাহচর্য তাঁহার নৈতিক চরিত্রকে অধিকতর নির্মল,পরিচ্ছন্ন ও দীপ্তিমান করিয়া তুলিয়াছিল।
বস্তুত আল্লাহ্র ভয়ই নৈতিক চরিত্রের মূল উৎস। যাঁহার দিল আল্লাহ্র ভয়ে ভীত-কম্পিত নয়, সে না করিতে পারে হেন পাপ কার্যের উল্লেখ করা যায় না। হযরত উসমান (র) আল্লাহ্র ভয়ে সর্বদা কম্পিত ও অশ্রুসিক্ত থাকিতেন। কবর দেখিলে তিনি অস্থির হইয়া পড়িতেন। তিনি প্রায়ই রাসূলে করীম (স)-কে উদ্ধৃত করিয়া বলিতেনঃ কবর হইল পরকালীন জীবনের প্রথম পর্যায়। এই পর্যায়টি সহজে ও নিরাপদে অতিক্রম করা গেলে পরবর্তী সব কয়টি পর্যায়ই সহজে অতিক্রান্ত হইবে বলিয়া আশা করা যায়। পক্ষান্তরে ইহাতেই বিপদ দেখা দিলে পরবর্তী সব পর্যায়ই কঠিন হইয়া দাঁড়াইবে।
হযরত উসমান (রা) ইসলামের প্রায় সব কয়টি যুদ্ধে রাসূলে করীম (স)-এর সহগামী ছিলেন এবং সর্বক্ষেত্রেই তিনি তাঁহার জন্য আত্মোৎসর্গীকৃত হইয়াছিলেন। দৈনন্দিন জীবনেও রাসূলে করীম (স)-এর দুঃখ-কষ্ট দূরীভূত করার জন্য তিনি সর্বদা সচেতন ও সজাগ-সক্রিয় থাকিতেন। রাসূলে করীম (স)-এর প্রতি ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা,ভক্তি ও সম্মান প্রদর্শনে তিনি অতিশয় সচকিত থাকিতেন। তিনি যে হস্তে রাসূলে করীম (স)-এর হস্ত স্পর্শ করিয়া ইসলামের বায়’আত গ্রহণ করিয়াছিলেন, উহাতে জীবনে কোন দিন একবিন্দু মালিন্যও লাগিতে দেন নাই। তিনি আপন খিলাফত আমলে রাসূলে করীম (স)-এর পরিবারবর্গের প্রয়োজন পূরণের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন, যেন তাঁহাদিগকে কোনরূপ দৈন্য ও অসুবিধার সম্মুখীন হইতে না হয়।
রাসূলে করীম (স)-এর প্রতি তাঁহার এইরূপ অকৃত্রিম ও সুগভীর ভক্তি-শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠাপূর্ণ ভালোবাসা ও আন্তরিকতার অনিবার্য পরিণতি এই ছিল যে, তিনি ছোট-বড় প্রত্যেকটি ব্যাপারেই তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া চলিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা চালাইতেন। সাধারণ কথা, কাজ ও গতিবিধিতেও রাসূলে করীম (স)-এর হুবহু অনুসরণ করিবার জন্য তাঁহার চেষ্টার কোন ত্রুটি হইত না। নবী করীম (স)-কে তিনি যেভাবে অযু করিতে দেখিয়াছেন, নামায পড়িতে দেখিয়াছেন, লাশের প্রতি আচরণ করিতে দেখিয়াছেন, তিনিও এইসব কাজ ঠিক সেইভাবেই সম্পন্ন করিতেন। কাহাকেও রাসূলে করীম (রা)-এর সুন্নাতের বিপরীতে বা ভিন্নতর রীতিতে কোন কাজ করিতে দেখিলে সঙ্গে সঙ্গেই তিনি উহাতে আপত্তি জানাইতেন এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিতেনঃ ‘তুমি কি রাসূলে করীম (স)-কে এই কাজ করিতে নিজ চক্ষে দেখ নাই’। বস্তুত রাসূলে করীম (স)-এর এইরূপ আক্ষরিক অনুসরণই ছিল একজন আদর্শবাদী সাহাবী হিসাবে তাঁহার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।
লজ্জাশীলতা ও বিনয়-নম্রতা ছিল হযরত উসমান (রা)-এর এক বিশিষ্ট ধরণের গুণ। ঐতিহাসিক ও জীবনচরিত রচয়িতাগণ তাঁহার লজ্জাশীলতার কথা বিশেষ গুরুত্ব সহকারে উল্লেখ করিয়াছেন। স্বয়ং রাসূলে করীম (স)-ও তাঁহার এই লজ্জাশীলতাকে বিশেষ মর্যাদা দিতেন বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছে।
হযরত উসমান (রা) তাঁহার স্বভাবসুলভ লাজুকতা, বার্ধক্যজনিত দুর্বলতা এবং সীমাহীন পারিবারিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে লালিত-পালিত হওয়ার কারণে উত্তম পোশাক-পরিচ্ছদ ও উৎকৃষ্ট খাদ্য গ্রহণে অভ্যস্থ ছিলেন। হযরত উমর ফারুক (রা)-এর ন্যায় কষ্ট-সহিষ্ণুতা ও প্রকৃতিগত কঠোরতা তাঁহার ছিলনা। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি জাঁকজমক ও বিলাস-ব্যসনপুর্ণ জীবন যাপন করিতেন, এমন কথা মনে করিবার কোন কারণ নাই।সত্য কথা এই যে, তিনি নিজে বিপুল ধন-সম্পদের অধিকারী হইয়াও কিছুমাত্র বড়লোকী জীবন-মান গ্রহণ করেন নাই। এই কারণে বিলাসিতা ও জাঁকজমকপূর্ণ জীবনধারা ছিল তাঁহার নিকট অত্যন্ত অপছন্দনীয়।
তিনি স্বভাবগতভাবে অতি বিনয়ী ও নিরহংকার ছিলেন। তাঁহার পারিবারিক কাজকর্মের জন্য বহু সংখ্যক লোক নিয়োজিত থাকা সত্ত্বেও নিজের যাবতীয় কাজকর্ম তিনি নিজেই সম্পাদন করিতেন এবং ইহাতে কোনরূপ লজ্জা বা অপমান বোধ করিতেন না। ব্যক্তিগত জীবনে কার্পণ্য কাহাকে বলে তাহা তিনি জানিতেন না। তিনি ছিলেন তদানীন্তন আরবের সর্বাধিক ধনাঢ্য ব্যক্তি। সেই কারণে দানশীলতা ছিল তাঁহার চরিত্রের প্রধান ভূষণ। তিন নিজের ধন-সম্পদ নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানে নয়- সাধারণ জনকল্যাণেই ব্যয় করিতে থাকিতেন। ইসলামের কাজে তাঁহার ধন-সম্পদ যতটা ব্যয়িত হইয়াছে, তদানীন্তন সমাজে এই দিক দিয়া অন্য কেহই তাঁহার সমতুল্য হইতে পারে না।
মদীনায় পানির সমস্ত কূপ লবনাক্ত ছিল। শুধু ‘রুমা’ নামক একটি কুপ হইতে মিষ্টি পানি পাওয়া যাইত; কিন্তু উহার মালিক ছিল জনৈক ইয়াহুদী। হযরত উসমান (রা) জনগণের প্রয়োজন পূরণের উদ্দেশ্যে উক্ত কূপটি বিশ হাজার দিরহামের বিনিময়ে ক্রয় করিয়া জনসাধারণের জন্য ওয়াকফ করিয়া দেন। নগরীতে মুসলমানদের সংখ্যা দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পাওয়ার দরুণ মসজিদে নববী সম্প্রসারিত করা অপরিহার্য হইয়া পড়িলে তিনি বিপুল অর্থ ব্যয় করিয়া এই অত্যাবশ্যকীয় কাজটি সম্পন্ন করিয়া ফেলেন। অনুরূপভাবে তাবুক যুদ্ধকালে নিজস্ব তহবিল হইতে অর্থব্যয় করিয়া তিনি সহস্র মুজাহিদকে সশস্র ও সুসংগঠিত করিয়া দেন। অথচ এই সময় মুসলমানদের দৈন্য ও দারিদ্র তাঁহাদিগকে নির্মমভাবে পীড়িত ও উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিয়াছিল।এক কথায় বলা যায়, উসমান (রা) ছিলেন এক অতুলনীয় দানশীল ব্যক্তি। ব্যক্তি-মালিকানার ধন-সম্পদ হওয়া সত্ত্বেও তাঁহার হস্তে উহা সাধারণ জনগণের কল্যাণে ব্যাপকভাবে ব্যয়িত হইয়াছে। পুঁজিবাদী বিলাস-ব্যাসন কিংবা শোষণ-পীড়নের মালিন্য তাঁহার ব্যক্তি মালিকানাকে কিছুমাত্র কলুষিত করিতে পারে নাই।১ {বদান্যতার প্রবাদ পুরুষঃ বদান্যতা বা দানশীলতা ব্যাপারে হযরত উসমান (রা) ছিলেন অবিশ্বাস্য রকমের উদারহস্ত। তাঁহার দান খয়রাতের এক-একটি ঘটনা ছিল রূপকথার মত। একদা জনৈক অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি সাহায্যের প্রত্যাশায় হযরত উসমান (রা)-এর শরণাপন্ন হইল। লোকটি যখন হযরত উসমান (রা)-এর বাড়ীর সন্নিকটে পৌঁছিল, তখন তিনি (উসমান)নিবিষ্টচিত্তে মাটি হইতে সরিষার দানা খুঁটিয়া খুঁটিয়া তুলিতেছিলেন। এই দৃশ্য অবলোকন করিয়া আগন্তুক লোকটি ভীষণভাবে হতাশাগ্রস্ত হইয়া পড়িল। সে উসমান (রা)-কে এক নিকৃষ্ট কৃপণ ব্যক্তি ভাবিয়া ফিরিয়া যাইতে উদ্যত হইল। সহসা উসমান (রা) আগন্তুক লোকটিকে দেখিতে পাইলেন। তিনি তাহাকে কাছে ডাকিয়া এইভাবে ফেরত যাওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। লোকটি সব ঘটনা আদ্যপান্ত খুলিয়া বলিল। উসমান (রা)লোকটির কথা শুনিয়া একটু মুচকি হাসিলেন। ঘটনাক্রমে এই সময় পণ্য-সামগ্রী বোঝাই সাতটি উট আসিয়া সেখানে থামিল। উসমান (রা)উটসহ সমগ্র পণ্য-সামগ্রীই আগন্তুককে দান করিয়া দিলেন। এই ঘটনায় লোকটি একেবারে হতবাক হইয়া গেল এবং উসমান (রা) সম্পর্কে তাহার বিরুপ ধারণার জন্য বারবার অনুশোচনা প্রকাশ করিতে লাগিল।–সম্পাদক}
হযরত উসমান (রা) ছিলেন ধৈর্য ও সহনশীলতার বাস্তব প্রতীক। দুঃখ-কষ্ট ও বিপদ-মুছিবত যত বড় এবং যত মারাত্মকই হউক না কেন, সবর,ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার শানিত অস্ত্রে তিনি উহার সব কিছুই ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দিতেন এবং সমস্ত প্রতিকূলতার মুকাবিলায় তিনি পর্বতের ন্যায় অবিচলরূপে দাঁড়াইয়া থাকিতেন।
তাঁহার জীবনধারা ছিল অত্যন্ত সুশৃঙ্খল, পরিমিত ও সংযত। দিনের বেলায় খিলাফতের দায়িত্ব পালনে গভীরভাবে ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও রাত্রের বেশীর ভাগ সময় তিনি নামায ও আত্মিক সাধনায় নিমগ্ন থাকিতেন। অনেক সময় তিনি সমগ্র রাত্রিও জাগিয়া কাটাইতেন এবং এক রাকয়াতেই পূর্ণ কুরআন মজীদ পড়িয়া ফেলিতেন। এই ধরণের ঘটনা তাঁহার জীবনে বহুবার সংঘটিত হইয়াছে।যে কয়জন সাহাবী ইসলামের পূর্বে জাহিলিয়াতের জামানায় লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন, হযরত উসমান (রা) ছিলেন তাঁহাদের অন্যতম। এই কাজে তাঁহার যোগ্যতা ও দক্ষতা স্বয়ং নবী করীম (স) কর্তৃকও স্বীকৃত ও প্রশংসিত হইয়াছে। এই জন্য অন্যান্যের সঙ্গে তাঁহাকেও অহী লেখার কাজে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। হযরত রাসূলে করীম (স)-এর প্রতি যখনই অহী নাযিল হইত, তখনই উহা লিখিয়া রাখার সুষ্ঠু ও নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছিল। হযরত উসমান (রা)এই কাজে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন।
অবশ্য লেখার কাজে পারদর্শী হইলেও বক্তৃতা-ভাষণে তিনি অতটা সক্ষম ছিলেন না। খলীফা নির্বাচিত হওয়ার পর সর্বপ্রথম মিম্বারের উপর আরোহণ করিয়া তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে কোন ভাষণ না দিয়া শুধু বলিলেনঃ
আমার পূর্ববর্তী খলীফাদ্বয়-আবূ বকর ও উমর (রা) পূর্বেই প্রস্তুতি লইয়া আসিতেন। আমিও ভবিষ্যতে প্রস্তুত হইয়াই আসিব। কিন্তু আমি মনে করি, বক্তৃতা-ভাষণে সক্ষম ইমামের (নেতার) চেয়ে কর্মদক্ষ ইমামই তোমাদের জন্য প্রয়োজন।
এই কথাটুকু বলিয়া তিনি মিম্বারের উপর হইতে নীচে অবতরণ করিলেন। অবশ্য ইহার পর তিনি বিভিন্ন সময় প্রয়োজন মত বক্তৃতা-ভাষণ দিয়াছেন এবং উহাতে তাঁহার যোগ্যতারও যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইত। তাঁহার ভাষণসমূহ খুবই সংক্ষিপ্ত,জ্ঞানগর্ভ এবং উচ্চমানের হইত।
হযরত উসমান (রা)-এর বর্ণিত একটি হাদীসে বলা হইয়াচেঃ ‘কুরআন মজীদ পড়া ও পড়ানো অতি উত্তম সওয়াবের কাজ’। এই হাদীস অনুযায়ী তিনি নিজে জীবনের শেষ মুহূর্তে পর্যন্ত আমল করিয়াছেন। সম্ভবতঃ এই কারণেই তিনি অধিকাংশ সময় কুরআন মজীদ তিলাওয়াতে অতিবাহিত করিতেন। তিনি পূর্ণ কুরআনেরও হাফিয ছিলেন। কুরআনের সহিত তাঁহার অন্তরের গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। জীবনের শেষ মুহূর্তে সশস্ত্র বিদ্রোহীরা যখন তাঁহাকে চতুর্দিক হইতে পরিবেষ্টন করিয়া ফেলিয়াছিল, তখনও তিনি সর্বদিক হইতে নিজেকে গুটাইয়া আনিয়া গভীর তন্ময়তা সহকারে কুরআন তিলাওয়াতে নিমগ্ন হইয়াছিলেন।
তিনি অহী-লেখক ছিলেন বিধায় কুরআন সম্পর্কিত জ্ঞানে তাঁহার অতুলনীয় পারদর্শিতা ছিল। বিভিন্ন জটিল বিষয়ে কুরআন হইতে দলীল পেশ করা এবং কুরআন হইতে শরীয়াতের বিধান খুঁজিয়া বাহির করায় তিনি বিশেষ দক্ষতা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। কুরআন-বিরোধীদের ষড়যন্ত্র হইতে কুরআন মজীদকে সুরক্ষিত করার ব্যাপারেও তাঁহার অবদান চির অম্লান হইয়া থাকিবে। হাদীস বর্ণনার ব্যাপারে তিনি অন্যান্য সাহাবীদের চেয়ে অধিক সতর্কতা অবলম্বন করিতেন। এই কারণে তিনি মাত্র ১৪৬টি হাদীস রাসূলে করীম (স) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। অবশ্য এই সতর্কতা অনেকটা ব্যক্তিগত ব্যাপার। ব্যক্তিগত রুচি ও দৃষ্টিকোণ হইতেই ইহা উৎসারিত। এই কারণে একই নবীর সাহাবী হওয়া সত্ত্বেও বর্ণিত হাদীসের সংখ্যার দিক দিয়া সাহাবীদের মধ্যে বিরাট তারতম্য হইয়াছে এবং ইহা ছিল খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার।
হযরত উসমান (রা) হযরত আবূ বকর (রা) হযরত উমর ফারুক (রা) এবং হযরত আলী (রা)-র ন্যায় বড় বড় মুজতাহিদদের মধ্যে গণ্য না হইলেও শরীয়াতের বহু ব্যাপারে তিনি ইজতিহাদ করিয়াছেন। এই ধরণের ইজতিহাদ এবং বিভিন্ন মিমাংসা ও ফয়সালা ইসলামের গ্রন্থাবলীতে উল্লেখিত হইয়াছে। বিভিন্ন বিষয়ে তাঁহার জ্ঞান ছিল অতুলনীয়। তিনি নিজে প্রত্যেক বৎসরই হজ্জ উদযাপন করিতেন ও ‘আমীরে হজ্জ’-এর দায়িত্ব পালন করিতেন। খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পরও তিনি একটিবারও হজ্জ উদযাপন হইতে বিরত থাকেন নাই। শরীয়াতের ব্যাপারে তিনি বিভিন্ন সময় যেসব রায় দিয়াছেন ও বিচার-ফয়সালা করিয়াছেন, তাহা ইসলামী শরীয়াতের বাস্তব ব্যাখ্যার দৃষ্টিতে চিরকাল অতীব মূল্যবান সম্পদ হইয়া থাকিবে। বিভিন্ন ইজতিহাদী ব্যাপারে অন্যান্য সাহাবীদের সহিত তাঁহার মতবৈষম্য ঘটিয়াছে। কিন্তু তিনি কুরআন-হাদীস যুক্তির ভিত্তিতে যে রায় দিতেন, তাহাতে তিনি সুদৃঢ় আত্মবিশ্বাসের দরুণই অবিচল হইয়া থাকিতেন। হযরত উসমান (রা) একজন সফল ও সার্থক ব্যবসায়ী ছিলেন বলিয়া হিসাব জ্ঞানে তাঁহার বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। এই কারণে ‘ইলমুল-ফারায়েজ’ বা উত্তরাধিকার বণ্টন-বিদ্যায় তাঁহার বুৎপত্তি ছিল সর্বজনস্বীকৃত। এই বিদ্যার মৌলিক নীতি প্রণয়নে হযরত জায়েদ ইবনে সাবিত (রা)-এর সঙ্গে তাঁহার অবদান অবশ্য স্বীকৃতব্য। সাহাবীগণ মনে করিতেন, ফারায়েজ বিদ্যায় এই দুইজন পারদর্শীর অন্তর্ধানের পূর্বে ইহার সঠিক প্রণয়ন না হইলে এই বিদ্যাই বিলুপ্ত হইয়া যাইবে।
হযরত উসমান (রা)-এর খিলাফত
হযরত উসমান (রা)-এর বয়স যখন চৌত্রিস বৎসর, তখন মক্কা নগরে দ্বীন-ইসলামের দাওয়াত সূচিত হয়। তদানীন্তন সামাজিক নিয়ম-প্রথা,আচার-আচরণ এবং আরবের ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির বিচারে হযরত উসমান (রা)-এর নিকট তওহীদের দাওয়াত প্রথম পর্যায়ে নিতান্তই অপরিচিত থাকিয়া গিয়াছিল। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তিনি তাঁহার ব্যক্তিগত পবিত্রতা,সত্যানুসন্ধিৎসা ও ন্যায়পরায়ণতার কারণে দ্বীন-ইসলামের দাওয়াত কবুল করার প্রস্তুত হইয়াছিলেন।
ইসলাম গ্রহন
নবুয়্যাতী মিশনের প্রথম পর্যায়েই হযরত আবূ বকর (রা) ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন।ইহার পরই তিনি ইসলাম প্রচারের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। প্রথমে তিনি তাঁহার বন্ধু-বান্ধব ও পরিচিতজনদের মধ্যে ইসলামী দাওয়াতের প্রচার শুরু করেন। হযরত উসমান (রা)-এর সাথে তাঁহার গভীর সম্পর্ক এবং পরিচিত ছিল। একদিন তিনি তাঁহার নিকট ইসলামী দাওয়াতের ব্যাখ্যা পেশ করেন। হযরত উসমান (রা)সবকিছুই শুনিয়া এই মহাসত্যের প্রতি প্রচণ্ড আকর্ষণ অনুভব করিলেন এবং নবী করীম (স)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া ইসলাম কবুল করার জন্য প্রস্তুত হইলেন। পথিমধ্যে নবী করীম (স) সহিত সাক্ষাৎ হইলে তিনিও উসমানকে ইসলাম কবুল করার জন্য মর্মস্পর্শী ভাষায় আহ্বান জানাইলেন। এই ঘটনার প্রসঙ্গে হযরত উসমান (রা) বলিলেনঃ “রাসূলে করীমের (স)-এর মুখ-নিঃসৃত কথা কয়টি শুনিবার সঙ্গে সঙ্গে আমার হৃদয়ে প্রবল আলোড়নের সৃষ্টি হইল। তখন স্বতঃস্ফূর্তভাবে আমি শাহাদাতের কালেমা পাঠ করিতে শুরু করিয়া দিলাম এবং রাসূলে করীম (স)-এর হাতে হাত দিয়া ইসলাম গ্রহণ করিলাম’।
হযরত উসমান (রা) মক্কার অন্যতম শক্তিশালী উমাইয়া বংশের লোক ছিলেন। আর গোটা বংশটিই ছিল রাসূলে করীম (স)-এর বংশ বনু হাশিমের চরম প্রতিদ্বন্দ্বী ও বিরুদ্ধবাদী। উমাইয়া বংশের লোকেরা রাসূলে করীম (স)-এর উত্তরোত্তর সাফল্য ও বিজয় লাভে বিশেষভাবে ভীত ছিল। কেননা উহার ফলে সমগ্র নেতৃত্ব ও প্রাধান্য উমাইয়া বংশের হস্তচ্যুত হইয়া বনু হাশিম বংশের হস্তগত হওয়ার প্রবল আশংকা ছিল। তদানীন্তন গোত্রবাদি সমাজে এই ব্যাপারটি যে কতটা সাংঘাতিক ছিল, গোত্রবাদের ধর্ম ও চরিত্র সম্পর্কে অবহিত লোকেরাই তাহা সহজেই অনুধাবন করিতে পারেন। কিন্তু হযরত উসমান (রা)-এর হৃদয়-দর্পণ বংশীয় ও গোত্রীয় হিংসাদ্বেষের কলুষ-কালিমা হইতে মুক্ত ও স্বচ্ছ ছিল বলিয়া শত বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও ইসলাম গ্রহণ করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া দাড়ায় নাই। তিনি যখন ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন তখন মুসলমানদের মোট সংখ্যা ছিল মাত্র পঁয়ত্রিশ কিংবা ছত্রিশ।
তাঁহার ইসলাম গ্রহণের পর নবী করীম (স) নিজেই আগ্রহী হইয়া তাঁহার কন্যা হযরত রুকাইয়া (রা)-র সহিত হযরত উসমান (রা)-এর বিবাহ সম্পন্ন করেন।
হিজরাত
মক্কা নগরে ইসলামের ক্রমবর্ধমান প্রসার ও শক্তি বৃদ্ধি ঘটিতে দেখিয়া মুশরিক সমাজ খুবই চিন্তান্বিত ও বিচলিত হইয়া পড়িল। তাহাদের ক্রোধ ও অসন্তোষ ক্রমশঃতীব্র হইতেও তীব্রতর হইয়া উঠিতে লাগিল। ইহার ফলে হযরত উসমান (রা)স্বীয় ব্যক্তিগত গুণগরিমা ও বংশগত মানমর্যাদা সত্ত্বেও ইসলামের জন্য অমানুষিক নির্যাতন ভোগ করিতে বাধ্য হন। ইসলাম ত্যাগে বাধ্য করার জন্য তাঁহার চাচা নিজে তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিত ও নির্মমভাবে প্রহার করিত। আত্মীয়স্বজনের মধ্য হইতে তেমন কেহই তাঁহাকে এই অবস্থা হইতে উদ্ধার করার জন্য আগাইয়া আসিতে প্রস্তুত হয় নাই। তাঁহার উপর এই অত্যাচারের মাত্রা ক্রমশঃবৃদ্ধি পাইতে থাকে। শেষ পর্যন্ত ইহা হযরত উসমান (রা)-এর পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠে। অবশেষে তিনি নবী করীম (স)-এর ইংগিতে একটি কাফেলা লইয়া সপরিবারে আবিসিনিয়ায় (ইথিওপিয়া) হিজরাত করিয়া গেলেন। কেবলমাত্র সত্য দ্বীন ও সত্য আদর্শের জন্য এই কাফেলাটি স্বদেশবাসীদের ত্যাগ করিয়া এক অজানা পথে রওনা হইয়া গেল।
আবিসিনিয়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইয়া যাওয়ার পর দীর্ঘদিন পর্যন্ত নবী করীম (স) তাঁহাদের সম্পর্কে কোন সংবাদ জানিতে পারেন নাই। এই কারণে তিনি খুবই চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন। কিছুদিন পর তিনি যখন তাঁহাদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছার সংবাদ জানিতে পারিলেন, তখন স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলিয়া উঠিলেনঃ
*******(আরবী)
‘এই জাতির মধ্য হইতে উসমানই সপরিবারে সর্বপ্রথম হিজরাতকারী ব্যক্তি’।
হযরত উসমান (রা) আবিসিনিয়ায় কয়েক বৎসর পর্যন্ত অবস্থান করেন। সেখান হইতে প্রত্যাবর্তনের পর কিছুদিন যাইতে না যাইতেই মদীনায় হিজরাত করার আয়োজন সুসম্পন্ন হয়। তখন উসমান (রা)-ও সপরিবারে মদীনায় চলিয়া গেলেন। হযরত উসমান (রা) ইসলাম ও কুফরের প্রথম সম্মুখ-সংঘর্ষে অর্থাৎ বদর যুদ্ধে যোগদান হইতে ঘটনাবশতঃই বিরত থাকিতে বাধ্য হন। এই যুদ্ধের সময় তাঁহার স্ত্রী নবী-তনয়া রুকাইয়া (রা) কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়েন। এই কারণে নবী করীম (স)তাঁহাকে যুদ্ধে যাওয়ার অনুমতি না দিয়া রোগিনীর সেবা-শুশ্রূষা করার দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দিলেন। কিন্তু এই দুঃখে তিনি ভারাক্রান্ত হইয়া সারাটি জীবন অতিবাহিত করেন। ইসলামের প্রথম সমরে শরীক হইতে না পারার বেদনা তিনি জীবনে মুহূর্তের তরেও ভুলিতে পারেন নাই।
কিন্তু ইহার পর যে কয়টি যুদ্ধই সংঘটিত হইয়াছে, উহার প্রত্যেকটিতেই তিনি পূর্ণ সাহসিকতা ও বীর্যবত্তা সহকারে রাসূলে করীম (স)-এর সঙ্গী হইয়াছেন। ষষ্ঠ হিজরী সনে নবী করীম (স) কা’বা জিয়ারতের উদ্দেশ্যে সদলবলে মক্কার পথে রওয়ানা হইয়া যান। পথিমধ্যে হুদাইবিয়া নামক স্থানে কাফেলাটি প্রতিরুদ্ধ হইলে নবী করীম (স)উসমান (রা)-কে রাষ্ট্রদূত হিসাবে কাফির মুশরিকদের সঙ্গে কথাবার্তা বলার দায়িত্ব দিয়া মক্কায় প্রেরণ করেন। মক্কায় তাঁহাকে কাফির মুশরিকরা অবরুদ্ধ করিয়া ফেলে। কয়েকদিন পর্যন্ত তাঁহার সম্পর্কে কোন সংবাদ জানিতে না পারায় নবী করীম (স) এবং মুসলমানগণ বিশেষভাবে উদ্বিগ্ন হইয়া পড়েন। এই সময় চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়ে যে, হযরত উসমান (রা)-কে শহীদ করা হইয়াছে। এই খবর শুনা মাত্রই নবী করীম (স) ইহার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য সঙ্গের চৌদ্দশত সাহাবীর নিকট হইতে বায়’আত গ্রহণ করেন।ইসলামের ইতিহাসে ইহা ‘বায়’আতে রিজওয়ান’- আল্লাহ্র সন্তোষলাভে চরম আত্মোৎসর্গের প্রতিশ্রুতি- নামে অভিহিত ও স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হইয়া রহিয়াছে।
খলীফারূপে নির্বাচন
হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর পর হযরত উমর ফারুক (রা) দীর্ঘ দশটি বৎসর পর্যন্ত ইসলামী খিলাফতের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি অজ্ঞাতনামা আততায়ীর ছুরিকাঘাতে আহত হইয়া পড়িলে জীবনের সায়াহ্নকালে পরবর্তী খলীফা নির্বাচনের জন্য ছয় সদস্য-বিশিষ্ট একটি বোর্ড গঠন করিয়া দেন। হযরত আলী, হযরত উসমান, হযরত জুবাইর, হযরত তালহা, হযরত সায়াদ, হযরত সায়াদ ইবনে আক্কাস এবং হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) এই বোর্ডের সম্মানিত সদস্য ছিলেন। তিন দিনের মধ্যেই খলীফা নির্বাচনের কাজ সম্পন্ন করার জন্যও এই বোর্ডকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। হযরত উমর ফারুক (রা)-এর কাফন-দাফন সম্পন্ন হওয়ার পর খলীফা নির্বাচনের ব্যাপারে মনোযোগ দেওয়া হয়। দুইদিন পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলাপ-আলোচনা, মত বিনিময়, জনমত যাচাই ইত্যাদি কাজে অতিবাহিত হইয়া যায়। তৃতীয় দিনে হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা)-এর প্রস্তাবক্রমের হযরত উসমান (রা)-কে খলীফা নির্বাচন করা হয়। সমবেত সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে হযরত আলী (রা) সর্বপ্রথম তাঁহার হাতে ‘বায়’আত’ করেন। অতঃপর উপস্থিত জনতা বায়’আতের জন্য ভাঙিয়া পড়ে। এইভাবে ২৪ হিজরী সনের মুহাররম মাসের ৪ তারিখ সর্বসম্মতিক্রমে হযরত উসমান (রা) খলীফা পদে বরিত হন এবং খিলাফতে রাশেদার শাসনভার গ্রহণ করে।
খিলাফতের দায়িত্ব পালন
হযরত উমর ফারুক (রা) তাঁহার খিলাফত আমলে সিরিয়া, মিশর ও পারস্য জয় করিয়া সুসংবদ্ধ ইসলামী রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন। উপরন্তু শাসন-শৃঙ্খলা ও প্রশাসন ব্যাবস্থায় তিনি একটা শাসনতান্ত্রিক কার্যবিধি প্রবর্তন করিয়া গিয়াছিলেন। এই কারণে হযরত উসমান (রা)-এর পক্ষে খিলাফতের দায়িত্ব পালন অনেকটা সহজ হইয়াছিল। এই কাজে তিনি যুগপৎ হযরত সিদ্দীকের নমনীয়তা, কোমলতা ও দয়ার্দ্রতা এবং হযরত উমর ফারুক (রা)-এর প্রশাসনিক দক্ষতা, বিচক্ষণতা ও কঠোরতা অনুসরণ করিয়া চলিতেন। এক বৎসরকাল পর্যন্ত তিনি পূর্ববর্তী প্রশাসন ব্যাবস্থা অপরিবর্তিত রাখিয়াছিলেন। প্রাক্তন খলীফার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তিনি হযরত সায়াদ ইবনে আক্কাস (রা)-কে কুফার গভর্নর নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ইহা ছিল খলীফা হযরত উসমান (রা) কর্তৃক সম্পাদিত প্রথম নিয়োগ। পরে অবশ্য ২৬ হিজরী সনে তিনি তাঁহাকে পদচ্যুতও করিয়াছিলেন।
উসমানীয় খিলাফতের প্রথম বৎসরের মধ্যেই ত্রিপলি, আলজিরিয়া ও মরক্কো অধিকৃত হয়। ইহার ফলে স্পেনের দিকে মুসলমানদের অগ্রগতির দ্বার উন্মুক্ত হয়। সাইপ্রাসের উপর হযরত উমর ফারুক (রা)-এর খিলাফত আমলেই কয়েকবার সৈন্য অভিযান পরিচালনা করা হইয়াছিল। ২৮ হিজরী সনে হযরত আমীর মুয়াবিয়ার নেতৃত্বে ভূ-মধ্য সাগরে অবস্থিত এই গুরুত্বপূর্ণ দ্বীপটির উপর মুসলিম বিজয়ের পতাকা উড্ডীন হয়। এইভাবে হযরত উসমান (আ)-এর খিলাফত আমলে ইসলামী রাজ্য সীমার বিপুলে বিস্তৃত ও সম্প্রসারন সাধিত হয়। কাবুল, হিরা, সিজিস্তান ও নিশাপুরে এই সময়ই ইসলামী খিলাফতের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।
হযরত উসমান (রা)-এর দ্বাদশ বর্ষীয় খিলাফত আমলের প্রথম ছয়টি বৎসর পূর্ণ শান্তি, শৃঙ্খলা ও নিয়মতান্ত্রিকতার মধ্যে অতিবাহিত হয়। বহু দেশ নিয়া গঠিত বিশাল এলাকা ইসলামী খিলাফতের অন্তর্ভুক্ত হয়। বায়তুলমালে আয়ের পরিমাণ বিপুলভাবে বৃদ্ধি পায়। কৃষি, ব্যবসায় ও প্রশাসন ক্ষেত্রের অসাধারণ উন্নতি জন-জীবনে অভূতপূর্ব সমৃদ্ধি আনিয়া দেয়। হযরত উসমান (রা)-এর খিলাফতের উল্লেখযোগ্য অবদান হইল ইসলামের বিশাল সাম্রাজ্যের প্রশাসন ব্যবস্থা উতরোত্তর দৃঢ়তর করিয়া তোলা এবং তীক্ষ্ণবুদ্ধিমত্তা, নির্ভুল ব্যবস্থাপনা ও উত্তম কর্মনীতির সাহায্যে বিজিত জাতিসমূহের বিদ্রোহাত্মক ভূমিকা ও তৎপরতা দমন করিয়া শান্তিপূর্ণ জীবন প্রতিষ্ঠা করা।
খলীফা হিসাবে হযরত উসমান (রা)-কে বহু সংখ্যক বিদ্রোহ দমন করিতে হইয়াছে। তাঁহার আমলে মিশরে বিদ্রোহের ঝাণ্ডা উত্তোলিত হয়, আর্মেনিয়া ও আযারবাইজান অঞ্চলের অধিবাসীরা ‘খারাজ’ দেওয়া বন্ধ করিয়া দেয়, খোরাসানবাসিরাও বিদ্রোহের মস্তক উত্তোলন করে। এইসব বিদ্রোহ ছিল বিজিত জাতিসমূহের মনে ধুমায়িত বিদ্বেষ ও প্রতিহিংসামূলক বিষ-বাষ্পের বিস্ফোরণেরই পরিণতি। কিন্তু হযরত উসমান (রা) বিশেষ সতর্কতা ও বিচক্ষণতা সাহায্যে উহা দমন করিতে সক্ষম। কঠোরতা-কোমলতা সমন্বিত কর্মনীতি ফলে এই সমস্ত এলাকার জনগণ ইসলামী খিলাফতের আনুগত্য স্বীকার করিয়া লয়।
সামুদ্রিক বিজয়াভিযান হযরত উসমান (রা)-এর খিলাফত আমলের একটি বিশেষ অবদান। হযরত উমর (রা)-র সতর্কতামূলক নীতির ফলে সে আমলে মুসলমানদিগকে বিপদসংকুল সামুদ্রিক পথে অভিযানে প্রেরণ শুরু হইতে পারে নাই। কিন্তু হযরত উসমান (রা)-এর দুঃসাহসিকতা বিপদ-শংকাকে সহজেই অতিক্রম করা সম্ভবপর করিয়া দিয়াছিল। তাঁহার নিখুঁত সমর পরিকল্পনার ফলে রোমান সম্রাটের পাঁচশতটি যুদ্ধ জাহাজ সমন্বিত বিশাল নৌ বাহিনীকে চরম পরাজয় বরণ করিতে বাধ্য করা হয়।
খিলাফতে শাসন পদ্ধতি
খিলাফতে রাশেদার শাসন-পদ্ধতি পরামর্শ ভিত্তিক রাষ্ট্রব্যবস্থা হিসাবে আরম্ভ হইয়াছিল। হযরত উমর ফারুক (রা)এই ব্যবস্থাকে অধিকতর সুদৃঢ় ও সুসংবদ্ধও করিয়া তোলেন। হযরত উসমান (রা)-ও তাঁহার প্রাথমিক আমলে এই ব্যবস্থাকে অব্যাহত রাখেন। তবে শেষ পর্যায়ে বনু উমাইয়্যাদের অভ্যুত্থানের ফলে ইহাতে অনেক বিপর্যয় সূচিত হয়। হযরত উসমান উহা রোধ করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা চালাইতে থাকেন এবং এই উদ্দেশ্যে দায়িত্বশীল লোকদের দেওয়া যে কোন কল্যাণমূলক পরামর্শ তিনি নির্দ্ধিধায় গ্রহন করেন।
প্রসঙ্গতঃউল্লেখ্য যে, খিলাফতী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের মৌলিক অধিকার রক্ষা শাসকদের কর্মনীতি ও কার্যাবলীর প্রকাশ্য সমালোচনা করার নিরংকুশ অধিকার লাভ করিয়া থাকে। এই অধিকার এতটুকু হরণ করার ইখতিয়ার স্বয়ং খলিফাকেও দেওয়া হয় নাই। ইহা অনস্বীকার্য যে, হযরত উসমান (রা)-এর শেষ পর্যায়ে পরামর্শ ভিত্তিক ব্যবস্থায় কিছুটা ফাটল ধরিতে শুরু করিয়াছিল। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও গণ-অধিকার কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হইতে দেওয়া হয় নাই।
আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত দায়িত্বশীল ব্যক্তিরাই সাধারণতঃ দায়িত্বহীন ব্যক্তিদের তুলনায় অধিকতর উত্তম ও নির্ভুল মতামত প্রকাশে সক্ষ হইয়া থাকেন। এই কারণে বর্তমান কালেও বিভিন্ন সভ্য ও উন্নত দেশে এই ধরণের পরামর্শমূলক সংস্থা গঠন করা হইয়া থাকে। হযরত উসমান (রা) চৌদ্দশত বৎসর পূর্বে এই প্রয়োজন অনুভব করিয়া দায়িত্বশীল সরকারী কর্মচারীদের সমন্বয়ে এই ধরণের একটি পরামর্শ মজলিস গঠন করিয়াছিলেন। এই সংস্থার সদস্যদের নিকট হইতে সাধারণতঃলিখিত প্রস্তাবাবলী চাওয়া হইত। কুফা অঞ্চলে সর্বপ্রথম যখন শাসন-শৃঙ্খলায় উচ্ছৃংখলতা ও বিপর্যয় দেখা দেয়, তখন উহা নির্মূল করার উদ্দেশ্যে মজলিশ সদস্যদের নিকট হইতে লিখিত প্রস্তাবাবলী চাওয়া হইয়াছিল। মূল রাজধানীতেও মাঝে মাঝে এই ধরণের মজলিসের অধিবেশন আহ্বান করা হইত। ২৪ হিজরী সনে সমগ্র দেশের সার্বিক অবস্থার সংস্কার ও উন্নয়ন সাধন উদ্দেশ্যে রাজধানীতে এই মজলিসের যে অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, উহাতে এই পর্যায়ের অভিমতদানে সক্ষম অধিকাংশ দায়িত্বশীল কর্মচারীরা যোগদান করিয়াছিলেন।
প্রশাসন ব্যবস্থাকে অধিকতর সক্রিয় ও সুদৃঢ় করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে সমগ্র দেশের প্রদেশ ও জিলাভিত্তিক বিভাজন ও পুনর্গঠন ছিল অত্যন্ত জরুরী কাজ। হযরত উমর ফারুক (রা) সমগ্র সিরিয়া অঞ্চলের দামেশক, জর্ডান ও ফিলিস্তিন এই এই তিনটি ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে বিভক্ত করিয়াছিলেন। হযরত উসমান (রা) এই সমস্ত অঞ্চল একজন গভর্নরের অধীন করিয়া একটি বিশাল বিস্তীর্ণ প্রদেশ বানাইয়াছিলেন। প্রদেশের এই পুনর্গঠন শাসন-শৃঙ্খলার দৃষ্টিতে খুবই ফলপ্রসূ হইয়াছিল। শেষকালে সমগ্র দেশ যখন বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতার লীলাভূমিতে পরিণত হইয়াছিল, তখন সিরিয়ার সহিত সংশ্লিষ্ট জিলাসমূহ এই বিপর্যয় হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল।
হযরত উসমান (রা) সেনাধ্যক্ষের একটা নূতন পদ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ইহার পূর্ব পর্যন্ত প্রাদেশিক গভর্নরই সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে অবস্থিত সেনাবাহিনীর অধিনায়কের দায়িত্ব ও পালন করিতেন। ইহাতে কাজের বিশেষ অসুবিধা হওয়া অবধারিত ছিল।
খিলাফতে রাশেদার শাসন পদ্ধতিতে খলীফাই রাষ্ট্রপ্রধান। তিনি প্রশাসন বিভাগের সর্ব্বোচ্চ ক্ষমতায় আসীন। অধিনস্থ সমস্ত শাসনকর্তা ও প্রশাসন কর্মকর্তাদের উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখা খলিফারই অন্যতম প্রধান গুরুত্বপূর্ণ কাজ। হযরত উসমান (রা) স্বভাবতঃই দয়ার্দ্র-হৃদয় ও নরম মেজাজের লোক ছিলেন। ব্যক্তিগত পর্যায়ে ধৈর্য,সহিষ্ণুতা,ক্ষমা ও তিতিক্ষার বাস্তব প্রতিমূর্তি ছিলেন তিনি। কিন্তু দেশ শাসন ও রাষ্ট্রীয় কার্যাদি সুসম্পন্ন করার ব্যাপারে তিনি ছিলেন অত্যন্ত কঠোর ও ক্ষমাহীন। কর্মচারীদের জিজ্ঞাসাবাদ, খোঁজ খবর লওয়া এবং দোষত্রুটি পরিলক্ষিত হইলে কঠোর হস্তে উহার সংশোধন করা তাঁহার স্থায়ী কর্মনীতি ছিল। এইক্ষেত্রে কোন সম্মানিত কর্মচারীরাও যদি তেমন কোন দোষ ধরা পড়িত, তাহা হইলে তাহাকে পদচ্যুত করিতেও তিনি একবিন্দু কণ্ঠিত হইতেন না। বায়তুলমালের সম্পদ অপচয় ও আত্মসাৎকরণ এবং শাসনকর্তাদের বিলাসপূর্ণ জীবন যাপন তাঁহার দৃষ্টিতে ছিল ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ।
হযরত উসমান (রা) দেশের প্রশাসনযন্ত্র নিয়ন্ত্রন ও দোষত্রুটি সংশোধনের উদ্দেশ্যে একটি কেন্দ্রীয় ‘অনুসন্ধান কমিটি’ গঠন করিয়াছিলেন এবং রাজধানীর বাহিরে সর্বত্র উহাকে পাঠাইয়া দিতেন। কমিটি সমগ্র অঞ্চল ঘুরিয়া ঘুরিয়া প্রশাসন কর্মকর্তাদের কাজকর্ম ও জনগণের অবস্থা সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করিত। এতদ্ব্যতীত দেশের সাধারণ অবস্থা সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অবহিতি লাভের উদ্দেশ্যে হযরত উসমান (রা) জুম’আর দিন মিম্বারে দাঁড়াইয়া খুতবা শুরু করার পূর্বেই উপস্থিত জনতার নিকট দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের পরিস্থিতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করিতেন। উপস্থিত লোকদের কথা তিনি বিশেষ মনোযোগ সহকারে শুনিতেন। উপরন্তু সমগ্র দেশবাসীর নিকট সাধারণভাবে ঘোষণা করিয়া দেওয়া হইয়াছিল যে, কোন প্রশাসকের বিরুদ্ধে কাহারো কোনোরূপ অভিযোগ থাকিলে হজ্জের সময় তাহা যেন খলীফার সম্মুখে পেশ করা হয়। কেননা এই সময় ইসলামী খিলাফতের সমস্ত দায়িত্বশীল কর্মকর্তাকে মক্কা শরীফে বাধ্যতামূলকভাবে উপস্থিত থাকিতে হইত। এইভাবে লোকদের নিকট হইতে সামনা-সামনি অভিযোগ শ্রবণ ও উহার প্রতিকার সাধনের একটি সুষ্ঠু ব্যবস্থা হযরত উসমান (রা)-এর আমলে কার্যকর ছিল।
উল্লেখ্য, সাধারণ প্রশাসন ও শাসন-শৃঙ্খলা ব্যবস্থায় এবং বিভিন্ন শাসন বিভাগের হযরত উমর ফারুক (রা) প্রবর্তিত সংস্থাসমূহে হযরত উসমান (রা) কোনরূপ পরিবর্তন আনেন নাই। তিনি বরং উহাকেই অধিকতর সুসংবদ্ধ ও শক্তিশালী করিয়া তোলেন। ইহার পরিণতিতে রাজস্ব আদায়ে বিশেষ উন্নতি সাধিত হয়। ইহা ছাড়া নূতন অধিকৃত এলাকা হইতে রাজস্ব আদায়ের মাত্রা অনেক গুন বৃদ্ধি পায়। ফলে বায়তুলমালে ব্যয়ের খাত পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশী সমৃদ্ধ হইয়া উঠে এবং বৃত্তি ও ভাতা হিসাবে বিপুল অর্থ জনসাধারণের মধ্যে বণ্টন করা হয়। হযরত উসমান (রা)-এর আমলে খিলাফতের পরিধি যতই সম্প্রসারিত হইয়াছে, উন্নয়ন ও পুননির্মাণের কাজ ততই ব্যাপকতা লাভ করিয়াছে। এই সময় প্রাদেশিক সরকারগুলিকে বিভিন্ন অফিসের জন্য বহুসংখ্যক ইমারত নির্মাণ করা হয়। ইহার পাশাপাশি সড়ক, পুল ও মসজিদ নির্মাণের কাজও ব্যাপকভাবে চলিতে থাকে। দূরগামী যাত্রীদের জন্য বহুসংখ্যক সাধারণ মুসাফিরখানা স্থাপন করা হয়।
রাজধানীতে যাতায়াতের সব কয়টি পথ অধিকতর সহজগম্য ও আরামদায়ক করিয়া তোলা প্রশাসন ব্যবস্থার সুষ্ঠুতা বিধান ও জনগণের চলাচল নির্বিঘ্ন করার জন্য একান্তই অপরিহার্য ছিল। হযরত উসমান (রা) ইহার জন্য যথাবিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। ইহা ছাড়া তাঁহার উদ্যোগে মদীনা ও নজদের পথে পুলিশ-চৌকি স্থাপন করা হয় এবং মিষ্টি পানির জন্য কূপ খনন করা হয়। খায়বরের দিক হইতে কখনো কখনো বন্যার পানি আসিয়া মদীনাকে প্লাবিত ও নিমজ্জিত করিয়া দিত। ইহার ফলে শহরবাসীরা বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইত। এমনকি মসজিদে নববীরও উহার দরুণ ধসিয়া পড়ার আশংকা দেখা দিয়াছিল। এই কারণে হযরত উসমান (রা) মদীনার অদূরে একটি বিরাট বাঁধ নির্মাণ করাইয়াছিলেন। সাধারণ জনকল্যাণের দৃষ্টিতে হযরত উসমান (রা) নির্মিত এই ‘মাহজুর’ বাঁধ তাঁহার একটি উল্লেখযোগ্য অবদান।
মসজিদে নববীর সম্প্রসারণ ও পুননির্মাণে হযরত উসমান (রা)-এর হস্তে খুবই প্রশস্ত এবং সুদক্ষ ছিল। নবী করীম (স)-এর সময় এই উদ্দেশ্যে সংলগ্ন ভূমি খরীদ করিয়া তিনি মসজিদের জন্য ওয়াকফ করিয়া দিয়াছিলেন, এতদ্ব্যতীত তাঁহার নিজের খিলাফত আমলেও এই কাজটি পুনর্বার সম্পাদিত হইয়াছে। এই সময় মসজিদ সম্প্রসারণের বিশেষ প্রয়োজন দেখা দিয়াছিল;কিন্তু মসজিদ সন্নিহিত ঘর-বাড়ির মালিক ও অধিবাসীরা মসজিদের নৈকট্য হইতে বঞ্চিত হওয়ার আশংকায় ইহাতে কোনক্রমেই প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া শুনাইয়া সম্মত করিবার জন্য হযরত উসমান (রা) অব্যাহতভাবে প্রচেষ্টা চালাইতে থাকেন। এইভাবে সুদীর্ঘ পাঁচটি বৎসর অতিবাহিত হইয়া যায়। কোনোরূপ বল প্রয়োগ বা প্রশাসন যন্ত্রের সাহায্যে জমি অধিগ্রহনের কাজ করিতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। ২৯ হিজরী সনে সাহাবীগণের সহিত এই বিষয়ে বিশেষভাবে পরামর্শ করা হয়। ইহার পরিপ্রেক্ষিত হযরত উসমান (রা) জুম’আর দিন অত্যন্ত সংবেদনশীল কণ্ঠে জনতার সম্মুখে ভাষণ পেশ করেন। ভাষণে তিনি নামাজীদের সংখ্যা বৃদ্ধি ও মসজিদের সংকীর্ণতা জনিত সমস্যা বিশেষভাবে বুঝাইয়া বলেন। ভাষণ শ্রবণের পর লোকেরা সানন্দ চিত্তে ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজেদের ঘরবাড়ী ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত হন।
হযরত উমর ফারুক (রা) সামরিক বিভাগের জন্য যে ব্যবস্থাপনা করিয়া গিয়াছিলেন, হযরত উসমান (রা) উহাকে আরও উন্নত ও সম্প্রসারিত করেন। সামরিক বিভাগকে তিনিই সর্বপ্রথম প্রশাসন বিভাগ হইতে বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র করিয়া গড়িয়া তোলেন। তাঁহার উদ্যোগে প্রতিটি কেন্দ্রীয় স্থানে সেনা সংস্থাকে একজন বিশেষ সামরিক কর্মকর্তার অধীনে ন্যস্ত করিয়া দেওয়া হয়। ফলে দূরবর্তী যে কোন স্থানে সামরিক বাহিনী প্রেরণের প্রয়োজন অত্যন্ত তড়িৎবেগে পূরণ করার সুষ্ঠু ব্যবস্থা গৃহীত হয়। এই সময় ত্রিপলি, সাইপ্রাস, তিবরিস্তান ও আর্মেনিয়া অঞ্চলেও সামরিক ঘাঁটি সংস্থাপন করা হয়।
হযরত উসমান (রা)-এর খিলাফত আমলে ঘোড়া এবং উহার উষ্ট্র পালন এবং উহার সংরক্ষণের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপিত হয়। এই উদ্দেশ্যে সমগ্র শাসনাধীন অঞ্চলে বিশাল চারণ ভূমি গড়িয়া তোলা হয়। রাজধানীর আশেপাশেও অসংখ্য চারণ ভূমি তৈয়ার করা হয় এবং চারণ ভূমির নিকটেই পানির ব্যবস্থা করা হয়।
দ্বীন-প্রচারের কাজ
খলীফা মূলত নবী করীম (স)-এর উত্তরাধিকারী, স্থলাভিষিক্ত এবং যাবতীয় সামষ্টিক দায়িত্ব পালনের জন্য দায়িত্বশীল। তাঁহার বড় কর্তব্য হইল দ্বীনের যথাযথ খেদমত এবং উহার ব্যাপক প্রচার সাধন। হযরত উসমান (রা) এই দায়িত্ব পালনে সদা-সচেতন ও বিশেষ কর্তব্যপরায়ণ হইয়া থাকিতেন। প্রত্যক্ষ জিহাদে যে সব অমুসলিম বন্দী হইয়া আসিত, তাহাদের সম্মুখে তিনি নিজে দ্বীনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও উহার সৌন্দর্য প্রকাশ করিতেন এবং দ্বীন-ইসলাম কবুল করার জন্য তাহাদিগকে আহ্বান জানাইতেন। ইহার ফলে শত শত লোক ইসলাম গ্রহণ করিয়া মুসলিম সমাজের অন্তর্ভুক্ত হইবার বিপুল সুযোগ লাভ করে।
বিধর্মীদের নিকট ইসলাম প্রচার ছাড়াও স্বয়ং মুসলিম জনগণের ধর্মীয় শিক্ষা-দীক্ষার জন্যও তিনি ব্যাপক ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন। দ্বীন সংক্রান্ত জরুরী মসলা-মাসায়েল তিনি নিজেই জনগণকে জানাইয়া দিতেন। কোন বিষয়ে দ্বীনের হুকুম তাঁহার নিকট অস্পষ্ট থাকিলে অন্যান্য বিশেষজ্ঞ সাহাবীদের নিকট তিনি জিজ্ঞাসা করিয়া লইতেন ও তদনুযায়ী আমল করিতেন এবং লোকদিগকেও তাহা অনুসরণ করিয়া চলিবার জন্য নির্দেশ দিতেন। এই ব্যপারে তিনি কোনোরূপ দ্বিধা-সংকোচের প্রশ্রয় দিতেন না।
প্রয়োজনে তাগিদে ইসলামের মূল বিধানের উপর নির্ভর করিয়া নবতর ব্যবস্থা প্রবর্তন করিতেও হযরত উসমান(রা) দ্বিধা করিতেন না। মদীনার লোকসংখ্যা যখন বিপুলভাবে বৃদ্ধি পাইল, তখন মসজিদের অভ্যন্তরে ইমামের সম্মুখে জুম’আর নামাযের একটি মাত্র আযানই যথেষ্ট মনে হইল না। এই কারণে তিনি উহার পূর্বে এক উচ্চস্থানে দাঁড়াইয়া জুমায়ার আর একটি আযান দেওয়ার ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন।
এই পর্যায়ে হযরত উসমান (রা)-এর বড় অবদান হইল কুরআন মজীদকে সর্বপ্রকার মতবিরোধ ও বিকৃতি হইতে চিরকালের জন্য সুরক্ষিত করিয়া তোলার এক অতুলনীয় কার্যক্রম। আর্মেনিয়া ও আযারবাইজান অভিযানে মিশর, সিরিয়া, ইরাক প্রভৃতি অঞ্চলের মুজাহিদগণ একত্রিত হইয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই নও-মুসলিম, অনারব বংশোদ্ভুত এবং আরবী ভাষায় অনভিজ্ঞ ছিলেন। হযরত হুজাইফা ইবনে ইয়ামান (রা)-ও এই জিহাদে শরীক ছিলেন। তিনি নিজে এই দুই জিহাদে অংশ গ্রহণকারী মুসলিম মুজাহিদদের কুরআন পাঠের ধরণ ও ভঙ্গিতে মারাত্মক রকমের পার্থক্য ও বৈষম্য লক্ষ্য করিলেন। দেখা গেল, প্রত্যেক এলাকার লোকেরা নিজস্ব ইচ্ছানুসারে কুরআন পড়ে এবং উহাকেই কুরআন পড়ার একমাত্র ধরণ ও ভঙ্গী মনে করিয়া লইয়াছে। যুদ্ধ শেষে তিনি মদীনার উপস্থিত হইয়া খলীফা হযরত উসমান (রা)-এর নিকট সমস্ত ব্যাপার বিস্তারিতভাবে পেশ করিলেন। তিনি গভীর আশংকা প্রকাশ করিয়া বলিলেন, অনতিবিলম্বে এই বিরোধ ও পার্থক্য সম্পূর্ণ দূরীভূত করিয়া এক অভিন্ন ধরণ ও ভঙ্গীতে কুরআন পাঠের ব্যবস্থা করা না হইলে মুসলিম সমাজও খৃস্টান রোমানদের ন্যায় আল্লাহ্র কিতাবের ব্যাপারে নানা বিভেদ ও বিসম্বাদের সৃষ্টি করিয়া ছাড়িবে। হযরত হুযাইফা(রা)-এর দৃষ্টি আকর্ষণে হযরত উসমান (রা) ইহার প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে বুঝিতে পারিলেন। তিনি উম্মুল মু’মিনীন হযরত হাফসা (রা)-এর নিকট হইতে কুরআন মজীদের মূল গ্রন্থ আনাইয়া হযরত জায়েদ ইবনে সাবিত (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জুবাইর (রা) ও হযরত সায়াদ ইবনুল আ’স(রা) কর্তৃক উহার বহু সংখ্যক কপি তৈয়ার করাইয়া বিভিন্ন মুসলিম অঞ্চলে পাঠাইয়া দিলেন এবং উহাকেই কুরআন মজীদের চূরান্তরুপ হিসাবে গ্রহণ ও অনুসরণ করার জন্য সর্বসাধারণকে নির্দেশ দিলেন। সেই সঙ্গে লোকদের ব্যক্তিগতভাবে লিখিয়া লওয়া কুরআনের সব কপি তিনি নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলিলেন।
বস্ততঃ হযরত উসমান (রা) যদি এই পদক্ষেপ গ্রহণ না করিতেন, তাহা হইলে তওরাত, ইনজিল ও অন্যান্য আসমানী গ্রন্থের ব্যাপারে উহাদের প্রতি বিশ্বাসী লোকেরা যে মারাত্মক ধরণের মতভেদ ও বৈষম্যে নিমজ্জিত হইয়াছে, শেষ নবীর উম্মতরাও অনুরূপ বিভেদ ও বৈষম্যে পড়িয়া যাইত এবং কুরআন মজীদেরও অনুরূপ দুর্দশা ঘটিত, ইহাতে একবিন্দু সন্দেহের অবকাশ নাই। তাই ইসলামের ইতিহাসে হযরত উসমান (রা)-এর এই মহান কীর্তি চিরকাল স্বর্ণক্ষরে লিখিত থাকিবে।
হযরত আলী (রা)-এর জীবন ও চরিত্র বৈশিষ্ট্য
প্রাথমিক জীবন
হযরত আলী (রা) বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর আপন চাচাতো ভাই ছিলেন। নবী করীম (স)-এর নবুয়্যাত লাভের বৎসর হযরত আলীর বয়স হইয়াছিল মাত্র দশ বৎসর। তাঁহার পিতা আবূ তালিব বহু সংখ্যক সন্তানের পিতা ছিলেন। আর্থিক অনটন ও দুর্ভিক্ষজনিত পরিস্থিতির দরুণ দারিদ্রের দুর্বহভারে তিনি ন্যুব্জ হইয়া পরিয়াছিলেন। এই অবস্থা দেখিয়া নবী করীম (স) তাঁহার অপর চাচা হযরত আব্বাস (রা)-এর সঙ্গে আবূ তালিবের দৈন্যভার লাঘব করার উপায় সম্পর্কে পরামর্শ করেন। নবী করীম (স) তাঁহাকে বলিলেন, ‘চাচার দারিদ্র্য ও দুঃখ-কষ্ট আমাদের সমভাগে ভাগ করিয়া লওয়া উচিত’। এই পরামর্শ অনুসারে হযরত আব্বাস (রা) আবূ তালিব পুত্র জাফরের এবং নবী করীম (স) স্বয়ং হযরত আলীর লালন-পালনের সমস্ত দায়িত্ব নিজ স্কন্ধে তুলিয়া লইলেন।
বস্তুত নবী করীম (স)-এর প্রতি আবূ তালিবের অবদান ছিল অনন্য। তিনি বনু হাশিমের সরদার ছিলেন এবং সমস্ত কুরাইশ গোত্রের উপর বনু হাশিমের প্রাধান্য ও প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল অসামান্য। কা’বা ঘরের সেবা ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং তৎসংক্রান্ত যাবতীয় দায়-দায়িত্ব বনু হাশিমের উপর অর্পিত ছিল। এই কারণে তদানীন্তন আরব সমাজে আবূ তালিবের প্রাধান্য ও নেতৃত্ব এক স্থায়ী ব্যবস্থা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। সমগ্র আরবের ধর্মীয় নেতৃত্ব এই পরিবারের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিল। নবী করীম (স) জন্মের পূর্বেই ইয়াতীম হইয়া গিয়াছিলেন। ফলে জন্মের অত্যল্পকাল পর হইতেই তিনি চাচা আবূ তালিবের স্নেহময় ক্রোড়ে লালিত-পালিত হইয়া যৌবনে পদার্পণ করেন। নবুয়্যাত লাভের পর তাহাঁরই প্রবল সমর্থনে ও আশ্রয়ে তিনি তওহীদের দাওয়াত প্রচারে ব্রতী হন। অতঃপর কুফরী শক্তির পক্ষ হইতে আসা অত্যাচার-নিপীড়নের প্রতিটি আঘাতের সম্মুখে আবূ তালিব বুক পাতিয়া দেন এবং এইভাবেই কাফিরদের আক্রমণের মুকাবিলায় তিনি ভ্রাতুষ্পুত্রকে রক্ষা করেন। তাঁহার এই সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষকতার দরুণ মুশরিক কুরাইশরা গোটা আবূ তালিব বংশের সহিত চরম শত্রুতায় মাতিয়া উঠে এবং যত উপায়ে সম্ভব তাহাদিগকে জুলুম, নির্যাতন ও নিপীড়নে জর্জরিত করিয়া তোলে। তাহাদের জুলুম-অত্যাচারের এক চূড়ান্ত রূপ দেখা গিয়াছে তখন, যখন মক্কার সমস্ত মুশরিকরা সম্মিলিতভাবে এই পরিবারটির সঙ্গে সকল প্রকার সম্পর্ক ছিন্ন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং শেষাবধি এই পরিবারটি পর্বত-গুহায় আশ্রয় লইতে বাধ্য হয়। কিন্তু সত্যের পৃষ্টপোষক এই পরিবারটির নেতা ও সরদার আবূ তালিব বিন্দুমাত্র দমিত না হইয়া সকল প্রকার বিরুদ্ধতা ও নির্যাতন নীরবে মাথা পাতিয়া নেন।
ইসলাম গ্রহণ
এই আবূ তালিবের পুত্র হযরত আলী (রা) বাল্যকাল হইতেই নবী করীম (স)-এর সঙ্গী-সাথী ও সহচর হিসাবে পরিচিত হইয়া উঠেন। এই কারণে নবুয়্যাত লাভের পর রাসূলে করীমের (স)-এর জীবনে পরিবর্তন সূচিত হওয়ার বিস্ময়কর দৃশ্যাবলী তিনি নিজ চক্ষে প্রত্যক্ষ করার সুযোগ লাভ করেন। এই পরিবর্তন সম্পর্কে হযরত আলী (রা)ই জিজ্ঞাসার জবাবে নবী করীম (স) যখন তাঁহার নিকট তওহীদী দ্বীনের ব্যাখ্যা করেন এবং ইহার প্রতি ঈমান আনার আহ্বান জানান, তখনি তিনি দ্বিধাহীন চিত্তে ও উদ্দীপিত হৃদয়ে দ্বীন-ইসলামের প্রতি ঈমান আনেন।
রাসূলে করীম (স)-এর প্রতি সর্বপ্রথম কে ঈমান আনিয়াছেন, এই পর্যায়ে বহু লোকের নাম হাদীসের গ্রন্থাবলীতে উল্লেখিত হইয়াছে। মুসলিম মনীষীদের শেষ সিদ্ধান্ত এই যে, বালক বয়সের যে কয়জন লোক প্রথম ঈমান আনিয়াছিলেন, হযরত আলী (রা) তাঁহাদের মধ্যে সর্বপ্রথম ব্যক্তি।
ইসলাম কবুল করার পর হযরত আলী (রা)-র জীবনের তেরটি বৎসর মক্কা শরীফে রাসূলে করীম (স)-এর গভীর সান্নিধ্যে অতিবাহিত হইয়াছে। তিনি যেহেতু সর্বক্ষণ রাসূলে করীম (স)-এর সঙ্গে থাকিতেন, এইজন্য পরামর্শ সভা, শিক্ষা-দীক্ষার মজলিস, কাফির মুশরিকদের সহিত বিতর্ক বৈঠক এবং এক আল্লাহ্র ইবাদাতের অনুষ্ঠানাদি-এক কথায় সর্ব ব্যাপারে তিনি রাসূলে করীম (স)-এর সহিত শরীক থাকিবার অফুরন্ত সুযোগ লাভ করেন। নবী করীম (স)নবুয়্যাতের প্রাথমিক পর্যায়ে যখন অতীব গোপনে ও লকচক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া এক আল্লাহ্র বন্দেগীতে নিমগ্ন হইতেন, হযরত আলী (রা) তাহাতেও উপস্থিত থাকিবার সুযোগ পাইতেন। এই গোপনীয়তা সত্ত্বেও আবূ তালিব একবার পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রকে বিশেষ ধরণের ইবাদতে মশগুল দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেনঃ ‘তোমরা দুইজন কি করিতেছ? তখন নবী করীম (স) তওহীদী দ্বীন ও আল্লাহ্র ইবাদতের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। আবূ তালিব সবকিছু শুনিয়া বলিলেনঃ ‘ঠিক আছে, ইহাতে কোন দোষ নাই। তোমরা করিতে পার; কিন্তু আমার পক্ষে সম্ভব হইবে না’।
নবুয়্যাত লাভের পর ক্রমাগত তিনটি বৎসর পর্যন্ত নবী করীম (স) দ্বীন-ইসলামের প্রকাশ্য দাওয়াত পেশ হইতে বিরত থাকেন। এই সময় দ্বীন প্রচারের সমস্ত কাজ তিনি বিশেষ গোপনীয়তা সহকারে চালাইতে থাকেন। তিনি বিশেষ লোকদের নিকট দ্বীনের দাওয়াত পেশ করার সঙ্গে সঙ্গে দ্বীনী আদর্শানুযায়ী লোকদের মন-মানসিকতা ও চরিত্র গঠনের দায়িত্বও পালন করিতেন। চতুর্থ বৎসর তাঁহার প্রতি আল্লাহ্ তা’আলার নির্দেশ অবতীর্ণ হইলঃ
******(আরবী)
তোমার বংশের নিকটবর্তী পূর্ণসংখ্যক লোকদিগকে (বেঈমানি ও শিরকের পরকালীন আযাব সম্পর্কে ) ভীত ও সাবধান করিয়া তোল।
নবী করীম (স) আল্লাহ্ তা’আলার এই নির্দেশ লাভ করিয়া নিকটবর্তী ‘সাফা’ পর্বতের চূড়ায় উঠিলেন এবং নিজ বংশের বিপুল জনতার সম্মুখে সর্বপ্রথম তওহীদী দ্বীনের আহবান উদাত্ত কণ্ঠে পেশ করিলেন। ইহার পরও নবী করীম (স) নিজের পরিবার ও বংশের লোকজনের নিকট সত্য দ্বীনের প্রতি ঈমান আনার দাওয়াত পেশের জন্য নানাভাবে প্রচেষ্টা চালাইয়াছেন। এমন কি একবার এই উপলক্ষে একটি ভোজের আয়োজন করার জন্য তিনি হযরত আলী (রা)-কে নির্দেশ দেন।
দ্বীন প্রচারে সহযোগিতা
হযরত আলী (রা)র বয়স তখন খুব বেশী হইলেও চৌদ্দ পনের বৎসরের অধিক হইবে না। কিন্তু এই অল্প বয়স সত্ত্বেও তিনি বিশেস দক্ষতা সহকারে নিজ বংশ ও পরিবারের লোকদের জন্য এক বিরাট ভোজের আয়োজন করেন। সংশ্লিষ্ট সমস্ত লোকই ভোজসভায় উপস্থিত হয়। প্রায় চল্লিশজন লোক ইহাতে যোগদান করে। কুরাইশ বংশের প্রভাবশালী প্রায় সব কয়জন সরদারই এখানে সমবেত হয়। খাওয়া-দাওয়া শেষ হইবার পর নবী করীম (স) দাঁড়াইয়া এক সংক্ষিপ্ত ভাষণের মাধ্যমে উপস্থিত জনগণের দ্বীন-ইসলাম কবুল করার আহবান জানান। আল্লাহ্ তা’আলা তাঁহার উপর দ্বীন প্রচারের যে বিরাট দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছেন, সেই কাজে তাঁহার সহিত সহযোগিতা করিবার জন্য তিনি প্রসঙ্গত সকলেই উদ্ধুদ্ধ করিতে চেষ্টা করেন। নবী করীম (স)-এর ভাষণ শেষে সভাস্থলে সর্বপ্রথম হযরত আলী (রা)র কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হইয়া উঠে। তিনি নির্ভীক কণ্ঠে বলিয়া উঠেনঃ ‘বয়সে আমি ছোট। দৈহিক অক্ষমতাও আমার অবর্ণনীয়। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও আমি এই মহান ব্রতে আপনার সঙ্গী, চির সহচর ও প্রান-পণ সাহায্যকারী থাকিব’। তাঁহার এই কথা শুনিয়া নবী করীম (স) বলিলেনঃ ‘তুমিই আমার ভাই ও আমার উত্তরাধিকারী’।
নবুয়্যাতের প্রায় তেরটি বৎসর মক্কায় অতিক্রান্ত হওয়ার পর আল্লাহ তা’আলা নবী করীম (স)-কে সমস্ত মুসলমান সমভিব্যাহারে মদীনায় হিজরাত করিয়া যাইবার জন্য নির্দেশ দেন। সে অনুসারে নবী করীম (স) মক্কার মুসলমানদিগকে একের পর এক মদীনায় চলিয়া যাইতে বলিলেন। ইহাতে মক্কা শহর মুসলমান-শূন্য হইয়া পড়ার আশংকা দেখা দিল। এই অবস্থা দেখিয়া কাফির মুশরিকগণ বিশেষভাবে শংকিত ও ভীত হইয়া পড়ে এই ভাবিয়া যে, মুসলমানরা বাহিরে কোথাও সংঘবদ্ধ ও বিপুল শক্তিতে বলীয়ান হইয়া আমাদের উপর আক্রমন করিয়া বসিতে পারে। এই আশংকায় তাহারা আগে-ভাগেই ‘শত্রু’ নিধনে কৃত-সংকল্প হইল। আল্লাহ্ তা’আলা অহীর মাধ্যমে নবী করীম (স)-কে এই বিষয়ে যথাসময়ে অবহিত করিলেন এবং অনতিবিলম্বে হিজরাত করার জন্য আদেশ দিলেন। তিনি হযরত আলী (রা)কে নিজের শয্যায় শায়িত রাখিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া যান এবং হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) সমভিব্যাহারে মদীনার দিকে রওয়ানা হন।
কাফির মুশরিকরা নবী করীম (স)-কে হত্যা করিয়া ইসলামের প্রোজ্জ্বল সূর্যের চির অস্তগমনের ব্যবস্থা করার জন্য সারা রাত্রব্যাপী তাঁহার বাসগৃহ অবরুদ্ধ ও পরিবেষ্টিত করিয়া রাখে। হযরত আলী (রা) তখন বাইশ-তেইশ বৎসরের এক যুবক মাত্র। তিনি কাফিরদের মারাত্মক ষড়যন্ত্র সম্পর্কে অবহিত হওয়া সত্ত্বেও অসীম সাহসিকতা সহকারে রাসূলের শয্যায় নিশ্চিন্তে ঘুমাইয়া থাকেন। সকাল বেলা শত্রুবাহিনী ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখিতে পায়, রাসূলে করীম (স) অনুপস্থিত এবং তাহাঁরই জন্য প্রান-উৎসর্গকারী এক যুবক তাহাঁরই শয্যায় আত্মদানের দৃঢ় সঙ্কল্প লইয়া নিদ্রায় অচেতন হইয়া রহিয়াছে। তখন তাহারা নিজেদের এই সম্মিলিত অভিযানের চূড়ান্ত ব্যর্থতা এবং রাসূলে করীম (স)-এর অবধারিত সাফল্য বুঝিতে পারিয়া মর্মাহত, লজ্জিত ও হতাশাগ্রস্ত হইয়া পড়ে।
মদীনায় কর্মময় জীবন
ইহার পর হযরত আলী (রা) দুই বা তিন দিন পর্যন্ত মক্কায় অবস্থান করেন। রাসূলে করীম (স)-এর নির্দেশ অনুযায়ী তাঁহার নিকট রক্ষিত জনগণের আমানতসমূহ যথাযথভাবে প্রত্যার্পণের পর তিনিও মক্কা ত্যাগ করিয়া মদীনা অভিমুখে যাত্রা করেন।
মদীনায় উপস্থিত হওয়ার পর সর্বপ্রথম মসজিদে নববীর নির্মাণে হযরত আলী (রা) প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করেন। তিনি রাসূলে করীম (স)-এর নির্দেশ অনুযায়ী উহার ভিত্তি স্থাপন করেন এবং অন্যান্য সঙ্গী-সাথীদের সহিত একত্র হইয়া উহার নির্মাণ কার্য সুসম্পন্ন করিয়া তোলেন।
অতঃপর বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর সুকঠিন কর্মময় জীবন শুরু হইলে হযরত আলী (রা) সেই ক্ষেত্রে ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও অদম্য সাহসিকতা সহকারে ছায়ার মতই তাঁহার সঙ্গী হইয়া থাকেন। নবী করীম (স)-এর প্রায় সব কয়টি যুদ্ধ-জিহাদেই তিনি পূর্ণ দায়িত্ব লইয়া অংশ গ্রহণ করেন। এসব ক্ষেত্রে তিনি যে বীরত্বের পরিচয় দিয়াছেন, উহাতে তাঁহার সমকক্ষ আর কেহই হইতে পারে না। বদর যুদ্ধে নবী করীম (স) তিনশত তের জন জীবন-উৎসর্গকারী সাহাবী সমভিব্যাহারে মদীনা হইতে রওয়ানা হইলেন। কাফেলার সম্মুখভাবে কালো বর্ণের দুইটি পতাকা মুসলিম বাহিনীর অগ্রাভিযানের নিদর্শন স্বরূপ পতপত করিয়া উড়িতেছিল। উহার একটি পতাকা হযরত আলী (রা)র হস্তে উড্ডীন হইতেছিল। বদর নামক স্থানে উপস্থিত হওয়ার পর নবী করীম (স) শত্রুপক্ষের গতি-বিধি লক্ষ্য করার উদ্দেশ্যে হযরত আলী (রা)র নেতৃত্বে একটি দুঃসাহসী ঝটিকা বাহিনী প্রেরণ করেন। ওহোদ যুদ্ধে নবী করীম (স) আহত হইয়া একটি গর্তে পড়িয়া গেলে শত্রু বাহিনীর লোকেরা তাঁহার দিকে তীব্র গতিতে অগ্রসর হয়। এই সময় প্রথমে হযরত মুসয়াব ইবনে উমাইর (রা) তাহাদের সহিত লড়াই করিতে করিতে শাহাদাত বরণ করেন। তাঁহার পরই হযরত আলী (রা) অগ্রসর হইয়া পতাকা ধারণ করেন এবং প্রতিরোধ যুদ্ধে বীরত্বের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া যুদ্ধের মোড় ঘুরাইয়া দেন।
বনু কুরাইজা অভিযানেও হযরত আলী (রা)র হস্তেই পতাকা উড়িতেছিল এবং রাসূলে করীম (স)-এর নির্দেশ অনুযায়ী ইয়াহুদীদের দুর্গ দখল করার পর উহার প্রাঙ্গনে তিনি আসরের নামায পড়েন। হুদাইবিয়ার হযরত উসমান (র)-এর শাহাদাতের সংবাদ পাওয়ার পর সাহাবীদের নিকট হইতে আত্মোৎসর্গ করার যে বায়’আত গ্রহণ করা হয়, হযরত আলী (রা)ও এই বায়’আতে শরীক ছিলেন। পরে মক্কার মুশরিকদের সহিত যে সন্ধি-চুক্তি লিখিত ও সাক্ষরিত হয়, নবী করীম (স) উহা লিখিবার জন্য তাঁহাকেই নির্দেশ দেন। খায়বর যুদ্ধে প্রথম দুইটি অভিযানে নেতৃত্ব দেন হযরত আবূ বকর (রা) ও হযরত উমর (রা)। কিন্তু কোন অভিযানেই বিজয় সম্ভবপর হয় নাই। সর্বশেষে নবী করীম (স) হযরত আলী (রা)র স্কন্ধে খায়বরের দুর্ভেদ্য দুর্গসমূহ জয় করার দায়িত্ব অর্পণ করেন। তিনি প্রবল বিক্রমে যুদ্ধ করিয়া খায়বরের দুর্গসমূহের উপর ইসলামের বিজয় পতাকা উড্ডীন করেন। মক্কা বিজয়ের অভিযানেও তিনি অগ্রবর্তী বাহিনীর পতাকা লইয়া বিজয়ীর বেশে নগর অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন। তাবুক যুদ্ধ হইতে প্রত্যাবর্তনের পর নবী করীম (স) সেই বৎসরের হজ্জে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-কে ‘আমীরে হজ্জে’ বানাইয়া মক্কায় প্রেরণ করেন। তাঁহার রওয়ানা হইয়া যাওয়ার পর সূরা ‘বারায়াত’(তওবা) নাযিল হয়। মদীনায় উপস্থিত সাহাবীগণ এই সূরাটি আদ্যোপান্ত শুনার পর মত প্রকাশ করেন যে, হজ্জের সময় সমবেত মুসলমানদের সম্মুখে এই সূরাটি পড়িয়া শুনানো হইলে খুবই ভালো হইবে। নবী করীম (স)ও ইহার গুরুত্ব অনুধাবন করিয়া হযরত আলী (রা)কে এই দায়িত্ব দিয়া মক্কা শরীফ পাঠাইয়া দিলেন।
ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে নবী করীম (স) যে কয়টি প্রতিনিধিদল বিভিন্ন অঞ্চলে প্রেরণ করেন, ইয়েমেনে প্রতিনিধিদল প্রেরণ তন্মধ্যে বিশেষ গুরুত্তের অধিকারী। হযরত খালিদ ইবনে অলীদ (রা) দীর্ঘ ছয় মাস যাবত নানাভাবে চেষ্টা চালাইয়াও সফলকাম হইতে ব্যর্থ হন সর্বশেষে হিজরী দশম বৎসরে নবী করীম (স) হযরত আলী (রা)-কে এই দায়িত্ব দিয়া পাঠাইবার সিদ্ধান্ত নেন। হযরত আলী (রা) ইয়েমেন উপস্থিত হইতেই সেখানকার অবস্থার আমূল পরিবর্তন সূচিত হয়। তিনি সেখানকার লোকদের সম্মুখে ইসলামের তত্ত্ব,মাহাত্ম্য ও বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করেন এবং ইহার ফলে হাজার হাজার লোক ইসলাম দীক্ষিত হন।
একাদশ হিজরীর রবীউল আউয়াল মাসে নবী করীম (স) পরলোক গমন করেন। এই মর্মান্তিক বেদনা সমস্ত মুসলিম জগতকে প্রচণ্ডভাবে ব্যথাতুর করিয়া ফেলে। নবী পরিবারের সদস্যগণ সর্বাধিক পরিমাণে কাতর ও বেদনা-বিধুর হইয়া পড়েন। প্রত্যেকেরই হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়, চক্ষুদ্বয় চিরকালের জন্য শ্রাবণের অস্রু নির্ঝরে পরিণত হয়। হযরত আলী (রা) নবী পরিবারের মধ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব ছিলেন। ব্যক্তিগত সম্পর্কও ঘনিষ্ঠতার দিক দিয়া যেমন, পারিবারিক ও আত্মীয়তার দিক দিয়াও তেমনি এই বেদনা তাঁহার পক্ষে অসহনীয় হইয়াছিল। তদুপরি নবী-তনয়া হযরত ফাতিমা (রা)র ইয়াতীমী তাঁহা অন্তরে দুঃসহ আঘাত হানে। তিনি ভয়ানক রকম মুষড়িয়া পড়েন এবং দীর্ঘ দিন পর্যন্ত সমাজ ও রাষ্ট্রের সহিত সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া নিতান্তই ঘর-বাসী হইয়া থাকেন। এই সময় নিজের দুঃখ সামলানো, হযরত ফাতিমা (রা)-কে সান্তনা দান এবং কুরআন মজীদ সুসংবদ্ধকরণ ব্যতীত অন্য কোন কাজের প্রতি বিন্দুমাত্র উৎসাহ বা কৌতূহল প্রদর্শন করা তাঁহার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল। কিছুদিন পর হযরত ফাতিমা (রা) ও যখন ইন্তেকাল করিয়া গেলেন তখন তিনি নিজেকে যেন নাড়া দিয়া উঠাইলেন এবং প্রথম খলীফা আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার হস্তে খিলাফতের বায়’আত করেন।
হযরত আবূ বকর (রা)-এর পরে হযরত উমর ফারুক (রা) তাঁহার খিলাফত আমলে সকল জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে হযরত আলী (রা)-এর সহিত পরামর্শ করিতেন। হযরত আলী (রা)ও তখন অত্যন্ত নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা সহকারে প্রতিটি ব্যাপারে তাঁহাকে পরামর্শ দিতেন। নিহাওয়ান্দ অভিযানে তাঁহাকে সেনাধ্যক্ষের দায়িত্ব গ্রহণের প্রস্তাব করা হয়। কিন্তু তিনি তাহা গ্রহণ করিতে অসম্মত হন। পরে উমর (রা) যখন বায়তুল মাকদিস গমন করেন, রাজধানীতে হযরত আলী (রা)কে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত (Acting)করিয়া খিলাফতের সমস্ত দায়িত্ব তাঁহার নিকট অর্পণ করিয়া যান। হযরত উমর (রা)-এর পর হযরত উসমান (রা)-এর খিলাফতের শেষ দিকে সারা দেশে যখন অশান্তি ও উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা দেয়, তখন তাহা দমন করার জন্য হযরত আলী (রা) বিশেষ ও কার্যকর পরামর্শ দান করেন এবং অশান্তির মূল কারণসমূহ নির্দেশ করিয়া তাহা সংশোধন ও বিদূরণের পন্থা দেখাইয়া দেন।
হযরত আলী (রা)-র খিলাফত
খলীফা নির্বাচন
হযরত উসমান (রা)-এর শাহাদাত বরণের পর তিনদিন পর্যন্ত খিলাফতের আসন শূন্য থাকে। এই সময় পরবর্তী খলীফার জন্য হযরত আলী (রা)-এর প্রতি জনগণের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়। বহু লোক তাঁহাকে এই দায়িত্ব গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানায়। প্রথম দিকে তিনি স্পষ্ট ভাষায় অসম্মতি জানানো সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত মুহাজির ও আনসার সাহাবীগণের পৌনঃপুনিক অনুরোধে এই দায়িত্ব গ্রহন করিতে তিনি সম্মত হন।
হযরত আলী (রা)-এর খলীফা নির্বাচিত হওয়ার বিবরণ ইসলামী রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ইতিহাসে সবিস্তারে উল্লেখিত হইয়াছে। জনতা হযরত আলী (রা)র নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলঃ
*******(আরবী)
আমরা আপনার হাতে আনুগত্যের বায়’আত করিব, আপনি হাত প্রসারিত করিয়া দিন। কেননা এখন আমাদের একজন আমীর-রাষ্ট্রনায়ক-নিযুক্ত করা একান্তই অপরিহার্য। আর এই পদের জন্য আপনি অধিকতর যোগ্য ও অধিকারী।
হযরত আলী (রা) ইহার উত্তরে বলিলেনঃ
*******(আরবী)
এই ব্যাপারে কিছু বলার বা করার তোমাদের কোন অধিকার নাই। ইহাতো পরামর্শদানের যোগ্যতাসম্পন্ন ও বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী প্রাথমিক পর্যায়ের মুসলমানদের সম্মিলতভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপার। তাঁহারা যাহাকে খলীফারূপে গ্রহণ করিবেন, তিনিই খলীফা হইবেন। অতএব চল, আমরা সকলে একত্রিত হই এবং বিষয়টি সম্পর্কে বিচার-বিবেচনা করি।
এই কথা শুনিয়া লোকেরা তাঁহার নিকট হইতে চলিয়া গেল। কিন্তু কিছুক্ষন পর তাহারা পুনরায় তাঁহার নিকট আসিয়া বায়’আত করার জন্য চাপ দিতে থাকে। তখন হযরত আলী (রা) বলিলেনঃ
******(আরবী)
তোমরা যদি ইহাই চাও যে, ‘আমি খলীফা হই ও তোমাদের নিকট হইতে আনুগত্যের বায়’আত গ্রহণ করি, তাহা হইলে মসজিদে নববীতে চল,সেখানেই এই বিষয়ে চূড়ান্ত ফয়সালা হইবে।
নিশ্চিন্ত কথা, আমাকে খলীফা নির্বাচন করা ও সেজন্য আনুগত্যের বায়’আত করা গোপনে অনুষ্ঠিত হইতে পারে না। ইহা অবশ্যই মুসলিম জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত সন্তোষ ও অনুমোদনের ভিত্তিতেই হইতে পারে।
অতঃপর মসজিদে নববীতে সমবেত সর্বসাধারণ মুসলমানদের প্রস্তাবনা এবং স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন ও আনুমোদনের পর হযরত আলী (রা)-কেই পরবর্তী খলীফা নির্বাচিত করা হয় এবং ২১ শে যিলহজ্জ সোমবার দিন মসজিদে নববীতে বিপুল ইসলামী জনতার উপস্থিতিতে তাঁহারই হস্তে খিলাফতের সাধারণ বায়আত গ্রহণ করা হয়। তিনি বরিত হন খিলাফতে রাশেদার চতুর্থ খলীফা হিসাবে।
হযরত আলী (রা) যখন খিলাফতের দায়িত্ব নিজের স্কন্ধে তুলিয়া নেন, তখন সমগ্র মুসলিম জাহান চরম অরাজকতা ও বিদ্রোহ-বিপ্লবের লীলাভূমিতে পরিণত হইয়াছিল। প্রথম খলীফা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) কেও অনুরূপ এক অশান্তি ও বিদ্রোহ-বিপ্লবের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল বটে; কিন্তু এই দুইটি অবস্থার মধ্যে বিরাট পার্থক্য ছিল। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)কে যে বিপদের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল,তাহা ছিল কাফিরী ও ইসলামত্যাগী এবং ইসলামের পারস্পরিক সংঘর্ষ। সমস্ত ইসলামী জনতা এই সংঘর্ষের খলীফার সমর্থক ও পৃষ্ঠপোষক ছিল। বিরুদ্ধবাদীরা ছিল বাতিলপন্থী,লালসা ও দুস্প্রবৃত্তির অনুসারী। তাহাদের মতের কোন স্থিতি বা দৃঢ়তা ছিল না। পক্ষান্তরে হযরত আলী (রা) কে যাঁহাদের বিরুদ্ধতার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল, তাঁহারা শুধু মুসলমানই ছিলেন না, বহু সংখ্যক সাহাবী এবং রাসূলে করীম (স)-এর সহধর্মিণী হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) পর্যন্ত তাঁহাদের মধ্যে শামিল ছিলেন। ইহাকে ভাগ্যের চরম পরিহাস ছাড়া আর কি-ইবা বলা যাইতে পারে।
কিন্তু এইসব বিপদ-আপদ, অশান্তি-উপদ্রব ও বিদ্রোহ-বিপ্লব সত্ত্বেও হযরত আলী(রা) অত্যন্ত দৃঢ়তা ও দুঃসাহসিকতা সহকারে খিলাফত তরুণীর হাল শক্ত করিয়া ধরিয়া রাখেন। এই সময় তিনি অপরিসীম ধৈর্য-সহিষ্ণুতা ও সুস্থ চিন্তা-বিবেচনার চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন এবং নানাক্ষেত্রে ব্যর্থতার নিদর্শন লক্ষ্য করা সত্ত্বেও পরম বিশ্বাসপরায়ণতা, অবিচল আদর্শবাদিতা এবং ইসলামী শরীয়াত ও রাষ্ট্রনীতির মৌল বিধান হইতে বিন্দুমাত্র বিচ্যুতিও সহ্য করিতে সম্মত হন নাই। তিনি যদি নীতি ও আদর্শবাদ হইতে একচুল পরিমাণ বিচ্যুতিও সহ্য করিতে প্রস্তুত হইতেন, তাহা হইলে রাষ্ট্রনীতির বিচারে তিনি হয়ত সফলকাম বিবেচিত হইতেন;কিন্তু দ্বীন-ইসলামের মহান আদর্শ ক্ষুণ্ণ,বর্জিত ও পরিত্যক্ত হইত, ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই। অথচ ইহাকে রক্ষা করাই হইল খলীফায়ে রাশেদ ও রাসূলে করীম (স)-এর স্থলাভিষিক্তের সর্বপ্রথম ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।
খলিফারুপে হযরত আলী (রা)
খিলাফতের শাসন-ব্যবস্থা পরিচালনায় হযরত আলী (রা) হযরত উমর ফারুক (রা)-এর পদাংক অনুসরণের কৃত-সংকল্প ছিলেন এবং তৎকালে প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থাপনায় কোনোরূপ মৌলিক পরিবর্তন সাধনে কিছুমাত্র সম্মত ছিলেন না। হযরত উমর ফারুক (রা) সমগ্র হিজাজ হইতে নির্বাসিত যেসব ইয়াহুদীকে নাজরান নামক স্থানে পুনর্বাসিত করিয়াছিলেন, তাহারা হযরত আলী (রা)র নিকট উপস্থিত হইয়া অত্যন্ত কাতর ও বিনীত কণ্ঠে তাহাদের প্রাক্তন বসতিতে প্রত্যাবর্তনের অনুমতি প্রার্থনা করে। কিন্তু হযরত আলী (রা) ইহাতে স্পষ্ট ভাষায় অস্বীকৃতি জানাইয়া বলিলেনঃ ‘হযরত উমর (রা) অপেক্ষা অধিক সুবিবেচক, বিচক্ষণ এবং সঠিক সিদ্ধান্তকারী আর কে হইতে পারে’?
দেশের আভ্যন্তরীণ শাসন-ব্যবস্থায় সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ হইল, দায়িত্বশীল কর্মকর্তাদের নিয়ন্ত্রণ এবং তাহাদের কার্যাবলী ও আচার-ব্যবহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ। হযরত আলী (রা) এই বিশেষ বিষয়টির উপর সব সময় দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিতেন। তিনি কোন দায়িত্বপূর্ণ পদে কাহাকেও নিয়োগ দান করার সময় অতীব মূল্যবান ও কল্যাণময় উপদেশাবলী প্রদান করিতেন। ইহা ছাড়া বিভিন্ন সময়ে এইসব কর্মকর্তাদের কার্যাবলী ও আচার-ব্যবহার সম্পর্কে বিশেষভাবে তদন্ত করাইতেন। এই গুরুত্বপূর্ণ কাজে একবার হযরত কায়াব ইবনে মালিক (রা) কে নিযুক্ত করিয়া নিম্নোক্ত ভাষায় তাঁহাকে নির্দেশ দিলেনঃ
********(আরবী)
তুমি তোমার সঙ্গীদের একটি দল লইয়া রওয়ানা হইয়া যাও এবং ইরাকের প্রতিটি জিলায় ঘুরিয়া ফিরিয়া কর্মচারীদের কাজকর্ম এবং তাহাদের স্বভাব-চরিত্র ও আচার-ব্যবহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য কর। তিনি সরকারী কর্মচারীদের অপচয় ও ব্যয়বাহুল্য এবং রাষ্ট্রীয় অর্থের ব্যাপারে তাহাদের অনিয়মতান্ত্রিকতা কঠোর হস্তে দমন করিতেন। বায়তুলমাল হইতে গৃহীত ঋণ যথাসময়ে আদায় করার জন্য কর্মচারীদের বিশেষভাবে কড়াকড়ি করিতেন। এই ব্যাপারে তিনি তাঁহার নিকটাত্মীয়দের প্রতি এতটুকু নমনীয়তা বা প্রীতি দেখাইতে প্রস্তুত ছিলেন না।
হযরত আলী (রা) রাজস্ব বিভাগের বিশেষ সংস্কার সাধন ও উন্নয়নমূলক নীতির প্রবর্তন করেন। রাজস্ব আদায়ে পূর্ণ কঠোরতা সত্ত্বেও সাধারণ জনগণের সার্বিক কল্যাণ ও সাধারণ অবস্থার উন্নয়ন সাধনে তিনি প্রতিনিয়ত যত্নবান ছিলেন। অক্ষম ও দরিদ্র জনতার প্রতি তিনি সব সময় অনুকম্পামূলক নীতি গ্রহণ করিতেন।
বস্তুত হযরত আলী (রা) ছিলেন জন-মানুষের জন্য আল্লাহ্র অপার রহমতের বাস্তব নিদর্শন ও জ্বলন্ত প্রতীক। তাহার খিলাফত আমলে সমাজের সাধারণ দীন-দরিদ্র ও অভাবগ্রস্ত লোকদের জন্য রাষ্ট্রীয় বায়তুলমালের দ্বার ছিল সদা উন্মুক্ত। বায়তুলমাল-এ যাহা কিছুই সঞ্চিত ও সংগৃহীত হইত, অভাবগ্রস্ত ও পাওয়ার যোগ্য লোকদের মধ্যে তাহা তিনি অনতিবিলম্বে ও উদার হস্তে বণ্টন করিয়া দিতেন। দেশের অমুসলিম নাগরিকদের সহিত তিনি অত্যন্ত সহৃদয়তা ও সহানুভূতিপূর্ন আচরণ অবলম্বন করিতেন। এমন কি, বিদ্রোহ ভাবাপন্ন ও ষড়যন্ত্রকারীদের কার্যকলাপও অতীব ধৈর্য-সহিষ্ণুতা সহকারে বরদাশত করা হইত।পারস্য অঞ্চলে খলীফার অনুসৃত এই উদার নীতির চমৎকার অনুকূল প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা গিয়াছিল।
হযরত আলী (রা) নিজে একজন সুদক্ষ ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সমর-নায়ক ছিলেন। সামরিক বিষয় ও ব্যাপারাদিতে তাঁহার দূরদর্শীতা ও বিচক্ষণতা ছিল তুলনাহীন। এই কারণে ইসলামী রাষ্ট্রের সামরিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বহু নবতর ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর হইয়াছিল।
হযরত আলী (রা)র মনীষা
হযরত আলী (রা) বাল্যকাল হইতেই নবুয়্যাতের শিক্ষা অঙ্গন হইতে সরাসরি জ্ঞান অর্জন ও প্রশিক্ষন লাভের সুযোগ পাইয়াছিল। রাসূলে করীম (স)-এর সহিত তাঁহার যে গভীরতর সম্পর্ক ও ঘনিষ্ঠতা ছিল, তাহারই দৌলতে তিনি এই পর্যায়ের অন্যান্য সকলের তুলনায় অধিক সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন। ঘরে-বাহিরে ও বিদেশ যাত্রাকালে তিনি নবী করীম (স)-এর নিবিড়তর নৈকট্য লাভ করিতে পারিয়াছিলেন বিধায় দ্বীন-ইসলামের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞানলাভ করা তাঁহার পক্ষে খুবই সহজ হইয়াছিল। নবী করীম (স) নিজেও তাঁহাকে এই বিশেষ জ্ঞান দান করার জন্য গুরুত্ব দিয়াছিলেন। তিনি নিজে তাঁহাকে কুরআন মজীদ শিক্ষা দিয়াছেন এবং কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের সঠিক তাৎপর্য বুঝাইয়া দিয়াছেন। এই কারণে অন্যান্য সাহাবায়ে কিরামের তুলনায় তাঁহার মনীষা ছিল অত্যন্ত ব্যাপক ও গভীরতর। রাসূলে করীম (স) তাঁহার এই মনীষার প্রতি ইঙ্গিত করিয়া বলিয়াছিলেনঃ
******(আরবী)
‘আমি জ্ঞানের নগরী আর আলী উহার দ্বার বিশেষ’।
একটি হাদীস হিসাবে সনদ ইত্যাদির বিচারে এই কথাটি গ্রহণযোগ্য না হইলেও ইহার বাস্তবতা অবশ্যই স্বীকৃতব্য। সাধারণ লেখাপড়া হযরত আলী (রা) বাল্যকালেই শিখিয়া লইয়াছিলেন এবং অহী লেখকদের তালিকায় তাঁহার নামও শামিল রহিয়াছেন। রাসূলে করীম (স)-এর নির্দেশ অনুযায়ী বহু রাষ্ট্রীয় ফরমানসহ হুদাইবিয়ার সন্ধিনামা হযরত আলী (রা)র হস্তেই সুলিখিত হইয়াছিল।
ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের মূল উৎস কুরআন মজীদ। হযরত আলী (রা) এই কুরআনের মহাসমুদ্র মন্থন করার সৌভাগ্য অর্জন করিয়াছিলেন। যে কয়জন সাহাবী নবী করীম (স)-এর জীবদ্দশায় পূর্ণ কুরআন মজীদ মুখস্থ করিয়া লইয়াছিলেন, হযরত আলী (রা) তাঁহাদের অন্যতম। কুরআনের কোন সূরা বা কোন আয়াতটি কি প্রসঙ্গে ও কোন সময় নাজিল হইয়াছিল, এই বিষয়ে তাঁহার বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। তিনি এই কথা নিজেই দাবি করিয়া বলিয়াছিলেন। এই কারণে কুরআনের মুফাসসিরদের উচ্চতম স্তরে তিনি পরিগণিত। উত্তরকালে রচিত বড় বড় তফসীর গ্রন্থে হযরত আলী (রা)র ব্যাখ্যামূলক বর্ণনাসমূহ বিশেষভাবে উদ্ধৃত হইয়াছে। কুরআনের মজীদকে নাজিল হওয়ার পরম্পরায় সুসজ্জিত করা তাঁহার এক বিশেষ অবদান। সেই সঙ্গে কুরআন মজীদ হইতে ব্যবহারিক জীবনের জন্য জরুরী আইন-বিধান বাহির করা এবং বিভিন্ন জটিল বিষয়ে ইসলামের নির্দেশ ও সিদ্ধান্ত জানার জন্য ইজতিহাদ কর্যা তাঁহার অসাধারণ দক্ষতা ও প্রতিভা সর্বজনস্বীকৃত। খারিজী ফির্কার লোকেরা নিতান্ত আক্ষরিক অর্থে কোন ব্যক্তিকে মীমাংসাকারী বা পারস্পরিক বিবাদ মিটাইবার জন্য মানিয়া লইতে অস্বীকৃতি জানাইল এবং তাহারা দলীল হিসাবে কুরআনের আয়াত ****(আরবী) ‘এক আল্লাহ্ ছাড়া মীমাংসাকারী আর কেহ হইতে পারে না’ পেশ করিল, তখন তিনি এইরূপ যুক্তি উপস্থাপনের অযৌক্তিকটা ও অবান্তরতা প্রমাণ করিয়া বলিলেনঃ ‘আল্লাহই যে চূড়ান্ত বিচারক তাহাতে আর সন্দেহ কি! কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক বিবাদ মিমাংসা করার জন্য আল্লাহ্ তা’আলা নিজেই যখন জনসমাজের লোককে সালিশ মানিবার জন্য নির্দেশ দিয়া বলিয়াছেনঃ
*******(আরবী)
স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের মধ্যে বিবাদ-বিরোধের আশংকা দেখা দিলে স্বামীর পক্ষ হইতে একজন এবং স্ত্রীর পক্ষ হইতে একজন মিমাংসাকারী প্রেরণ কর।
তখন মুসলিম জাতি ও জনতার পারস্পরিক বিবাদ মীমাংসার জন্য জনসমাজ হইতেই কাহাকেও নিযুক্ত করা ও মানিয়া লওয়া হইলে তাহা অন্যায় বা কুরআন-বিরোধী কাজ হইবে কেন? আল্লাহ্র সার্বভৌমত্ব ও সর্ব বিষয়ে তাঁহার চূড়ান্ত ক্ষমতা তো কোন-না-কোন মানুষের দ্বারাই কার্যকর ও বাস্তবায়িত হইবে। গোটা মুসলিম জাতির পারস্পরিক বিবাদ-বিসম্বাদের ব্যাপারটি কি একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোকের তুলনায়ও নগণ্য ব্যাপার?বস্তুতঃকুরআনের তাফসীর ও আয়াতসমূহের তাৎপর্য ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ পর্যায়ে হযরত আলী (রা)-র এত মূল্যবান বর্ণনাসমূহ উদ্ধৃত হইয়াছে যে, তাহা একত্র সন্নিবেশিত করা হইলে একখান বিরাট গ্রন্থের রূপ পরিগ্রহ করিতে পারে।
এক শ্রেণীর প্রতারক তাসাউফপন্থী প্রচার করিয়া বেড়ায় যে, রাসূলে করীম (স) হযরত আলী (রা)-কে দ্বীন-ইসলাম সংক্রান্ত মৌল জ্ঞান ও বিদ্যা ছাড়াও এমন কিছু জ্ঞানও তাঁহাকে শিক্ষা দিয়া গিয়াছিলেন যাহাকে বর্তমানে ‘তাসাউফ’ নামে অভিহিত করা হয়। তাহারা হযরত আলী (রা)-কে তাসাউফ শাস্ত্রের ‘আদি পিতা’ বলিয়াও প্রচারনা চালাইতেছে। কিন্তু ইহা কতবড় মিথ্যা অপবাদ এবং কতখানি ভিত্তিহীন কথা, তাহা একটি সহীহ হাদীসে উদ্ধৃত তাঁহার নিজের উক্তি হইতেই অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়। লোকেরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলঃ ‘আপনার নিকট কুরআন ছাড়া আরও কোন ইলম আছে নাকি?’ তিনি জওয়াবে বলিলেনঃ ‘সেই মহান সত্তার শপথ, যিনি বীজ ও আঁটিকে দীর্ণ করিয়া বৃক্ষ উৎপাদন করেন এবং যিনি দেহের ভিতরে প্রানের সঞ্চার করেন, আমার নিকট কুরআন ছাড়া অন্য কোন জিনিসই নাই। তবে কুরআনের সমঝ-বুঝের শক্তি-সামর্থ্য ও যোগ্যতা-প্রতিভা আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা দিয়া থাকেন। ইহা ছাড়া কয়েকটি হাদীস আমার নিকট রহিয়াছে’। (বুখারী, মুসনাদে আহমাদ)
হযরত আলী (রা) তাঁহার কথার শুরুতে যে শপথ করিয়াছেন, উহা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। তাঁহার এই কথা হইতে বুঝা গেল, কুরআনের আয়াতসমূহ আঁটি ও দেহের মত। আর উহার অর্থ, তাৎপর্য ও তত্ত্ব বৃক্ষের মত- যাহা সেই আঁটি ও বীজ হইতে নির্গত হয়। আর উহা সেই প্রাণের মত, যাহা দেহে প্রচ্ছন্ন হইয়া থাকে। অর্থাৎ একটা ক্ষুদ্রাকার বীজ ও আঁটি হইতে যেমন শাখা-প্রশাখা সমন্বিত একটি বিরাট বৃক্ষের উদগম হইতে পারে-যাহা মূলতঃসেই বীজ ও আঁটির মধ্যেই লুক্কায়িত ছিল; আর প্রানশক্তি হইতে-যাহা দেহে প্রচ্ছন্ন হইয়া থাকে-যেমন সমস্ত মানবীয় কর্ম ও কীর্তিকলাপ প্রকাশিত হয়, কুরআনের শব্দসমূহ হইতেও-যাহা দেহের মতই-বিপুল অর্থ ও তাৎপর্য বাহির হইতে পারে।
বস্ততঃ হযরত আলী (রা) যে কুরআনের তত্ত্ব ও দর্শনে বিশেষ বুৎপত্তির অধিকারী ছিলেন, ইহা তাঁহার উক্ত কথাটি হইতেই প্রমাণিত হয়।
হাদীসের ক্ষেত্রেও হযরত আলী (রা)র মনীষা ও বৈদগ্ধ্য ছিল অসাধারণ, বিশাল ও গভীর মহাসমুদ্র সমতুল্য। বাল্যকাল হইতে পূর্ণ ত্রিশটি বৎসর তিনি নবী করীম (স)-এর সাহচর্যে ও নিবিড় সান্নিধ্যে কাটাইয়াছেন। এই কারণে ইসলামের পূর্ণ আইন-বিধান ও রাসূলের বাণী সম্পর্কে হযরত আবূ বকর (রা)-এর পর তিনিই ছিলেন শ্রেষ্ঠ বিশারদ। ইহাছাড়া নবী করীম (স)-এর ইন্তেকালের পর সমস্ত বড় বড় সাহাবীদের মধ্যে তিনিই সর্বাধিক বয়স পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। রাসূলে করীম (স)-এর পর প্রায় ত্রিশটি বৎসর পর্যন্ত তিনি কুরআন, হাদীস এবং দ্বীন ও শরীয়াত প্রচারে নিরন্তর ব্যতিব্যস্ত ছিলেন। প্রথম তিনজন খলীফার আমলেও এই দায়িত্ব তাঁহার উপর ন্যস্ত ছিল। তাঁহার নিজের খিলাফত আমলেও নানা ফিতনা-ফাসাদ ও রক্তাক্ত যুদ্ধ-বিগ্রহ সত্ত্বেও জ্ঞান বিস্তারের এই স্রোত কখনো বন্ধ হয় নাই; বরং ইহা অব্যাহত ধারায় প্রবাহমান ছিল। এই কারণে প্রথম তিনজন খলীফার তুলনায় হাদীস বর্ণনায় অধিক সুযোগ তিনিই লাভ করিয়াছেন। কিন্তু এইসব সত্ত্বেও হাদীস বর্ণনায় তিনি অত্যন্ত বেশী সতর্ক ও কঠোর প্রকৃতির ছিলেন। এই কারণে তাঁহার বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা খুব বেশী হয় নাই। মাত্র ৫৮৬টি হাদীস তাঁহার সূত্রে গ্রন্থাবলীতে উদ্ধৃত হইয়াছে। নবুয়্যাতের জমানায় যে কয়জন সাহাবী হাদীস লিখিয়া রাখিতে অভ্যস্ত ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে হযরত আলী (রা)ও একজন। তাঁহার লিখিয়া রাখা হাদীস সম্পদকে তিনি “সহীফা” নামে উল্লেখিত করিতেন এবং এই ‘সহীফা’ তাঁহার তরবারির খাপের মধ্যে ঢুকাইয়া রাখিতেন। এই হাদীসসমূহ হইতে ব্যবহারিক জীবনের বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের মসআলা জানা যায়।
ফিকাহ ও ইজতিহাদের ক্ষেত্রে তাঁহার যোগ্যতা ও প্রতিভা সর্বজনস্বীকৃত। বড় বড় সাহাবীগণ- এমন কি তাঁহার বিরুদ্ধবাদীরাও-বিভিন্ন বিষয়ে তাঁহার নিকট হইতে শরীয়াতের সিদ্ধান্ত জানিয়া লইবার প্রয়োজনবোধ করিতেন। এই ক্ষেত্রে তাঁহার বিশেষ বুৎপত্তির বড় কারণ এই ছিল যে, তিনি নিজে অনেক বিষয়ে রাসূলে করীম (রা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়া লইতেন।
বিচারপতি হিসাবে হযরত আলী (রা)
হযরত আলী (রা) জীবনের বেশীর ভাগ সময় মদীনায় অতিবাহিত করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার খিলাফতের পুরা সময়টি তিনি কুফায় অবস্থান করিয়াছেন। এই কারণে তাঁহার ফিকাহ সংক্রান্ত মত ও ইজতিহাদ ইরাকেই বেশী প্রচার লাভ করিয়াছে। হানাফী মযহাবের ভিত্তি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের (রা) পরে হযরত আলী (রা)-র মত ও তাঁহার গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের উপরই সংস্থাপিত হইয়াছে। হযরত আলী (রা)-র এই যোগ্যতার কারণে শরিয়াত অনুযায়ী মামলা-মুকাদ্দমার বিচার করার ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে তাঁহার দক্ষতাও সর্বজন স্বীকৃত ছিল। হযরত উমর ফারুক (রা) বলিয়াছেনঃ
********(আরবী)
আমাদের মধ্যে বিচারক হিসাবে অধিক যোগ্য ব্যক্তি হযরত আলী এবং অধিক কুরআন-বিশারদ হযরত উবাই ইবনে কায়াব।
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ(রা) বলিয়াছেনঃ ‘আমরা পরস্পরে বলিতাম যে, মদিনায় সর্বাধিক বিচার-ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি হইতেছেন হযরত আলী (রা)।
স্বয়ং নবী করীম (স)-ও অনেক সময় বিচারকার্যের দায়িত্ব হযরত আলী (রা)র উপর অর্পণ করিতেন। নবী করীম (স) তাঁহাকে ইয়েমেনের বিচারপতির দায়িত্বে নিযুক্ত করিলে তিনি নিজের অযোগ্যতা ও অক্ষমতার কথা বলিয়া সেই দায়িত্ব গ্রহণ হইতে নিষ্কৃতি পাইতে চাহিয়াছিলেন। তখন নবী করীম (স) বলিলেনঃ
আল্লাহ্ তা’আলাই তোমার মুখকে সঠিক পথে এবং তোমার দিলকে দৃঢ় ও ধৈর্যসম্পন্ন করিয়া রাখিবেন।
হযরত আলী (রা) নিজেও বলিয়াছেনঃ
অতঃপর বিচার কার্যে আমি কখনও কোনোরূপ সংশয় বা কুণ্ঠাগ্রস্ত হই নাই।
বিচারকার্য পরিচালনা সম্পর্কে নবী করীম (স) তাঁহাকে বহু মূলনীতি ও নিয়ম-পদ্ধতি শিক্ষা দিয়াছিলেন। একবার তাঁহাকে বলিয়াছিলেনঃ
হে আলী! তুমি যখন দুই ব্যক্তির বিবাদ মীমাংসা করিতে বসিবে, তখন কেবল একজনের কথা শুনিয়াই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে না এবং দ্বিতীয় জনের বক্তব্য না শুনা পর্যন্ত তোমার সিদ্ধান্ত গ্রহণ স্থগিত রাখিবে।
মামলা বিচারের ক্ষেত্রে সন্দেহমুক্ত দৃঢ় প্রত্যয় লাভের জন্য মামলার দুইপক্ষ এবং সাক্ষীদের জেরা করা ও এই ব্যাপারে তাহাদিগকে প্রশ্ন না করা হযরত আলী (রা)-এর সুবিচার নীতির অপরিহার্য অংশরূপে নির্দিষ্ট। অপরাধ স্বীকারকারী(confessor)বার বার প্রশ্ন ও জেরা করার পরও নিজের স্বীকৃতির উপর অবিচল না থাকিলে তিনি এই স্বীকৃতির ভিত্তিতে তাহাকে কোন শাস্তি দিতেন না। সাক্ষীদিগকে নানাভাবে ভীত-সন্ত্রস্ত করার পর সাক্ষ্য-উক্তিতে তাহাদের অবিচল না পাইলে সে সাক্ষ্যের ভিত্তিতে তিনি কোন ফয়সালা করিতেন না। হত্যাসংক্রান্ত মামলার বিচারে তিনি দুর্ঘটনা ও হত্যার ইচ্ছা(Motive)-র মধ্যে পার্থক্য করিতেন। ১ {১.নায়বিচার প্রতিষ্ঠায় সচেতনতাঃ সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠাকে নিশ্চিন্ত করার লক্ষ্যে হযরত আলী (রা) সর্বদা সচেতন থাকিতেন। বিচার ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করার জন্য রাষ্ট্র-ক্ষমতার অপব্যবহারকে তিনি জঘন্য অপরাধ বলিয়া মনে করিতেন। ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তিনি মুসলিম ও অমুসলিম মধ্যেও কোনোরূপ ভেদনীতিকে প্রশ্রয় দিতেন না। এই ব্যাপারে একটি ঐতিহাসিক ঘটনা এখানে উল্লেখযোগ্য। একদা জনৈক ইয়াহুদী আমীরুল মুমিনীন হযরত আলী (রা)র লৌহবর্মটি চুরি করিয়া লইয়া গেল। দেশের সর্বোচ্চ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকা সত্ত্বেও ইনি সরাসরি এ ব্যাপারটি কোন পুলিশী ব্যবস্থা গ্রহণ করিলেন না; বরং প্রচলিত নিয়মনুযায়ী আদালতে গিয়া অভিযোগ দায়ের করিলেন। আদালতের বিচারক তাঁহাকে অভিযোগের সপক্ষে দুইজন সাক্ষী হাজির করার আদেশ দিলেন। হযরত আলী (রা) তাঁহার দুই পুত্র ইমাম হাসান ও ইমাম হুসাইন(রা)-কে সাক্ষী হিসাবে উপস্থিত করিলেন। কিন্তু বিচারক অভিযোগকারীর নিকটাত্মীয় বলিয়া ইহাদের সাক্ষ্য গ্রহণ না করিয়া বরং মামলাটিই খারিজ করিয়া দিলেন। এই ঘটনায় অভিভুক্ত হইয়া অভিযুক্ত ইয়াহুদী নিজেই তাহার অপরাধ স্বীকার করিল এবং পবিত্র কালিমা পড়িয়া ইসলামের কাফেলায় শরীক হইল।–সম্পাদক}
হযরত আলী (রা)-র বিচার-ফয়সালা আইনের দৃষ্টান্তরূপে গণ্য। এই কারণে মনিষীগণ উহা লিপিবদ্ধ করিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু উত্তরকালে দুষ্ট লোকেরা উহাতে নানারুপ বিকৃতির অনুপ্রবেশ ঘটায়। ইহার ফলে আইন বা বিচার জগতে উহা সম্পূর্ণ অকেজো হইয়া যায়।
ব্যাক্তিগত জীবনের কৃচ্ছ্র সাধনা
হযরত আলী (রা) ব্যক্তিগত জীবন অত্যন্ত কঠোর কৃচ্ছ্র সাধনার ভিতর দিয়া অতিবাহিত করিয়াছেন। দারিদ্রের নির্মম কষাঘাতে জর্জরিত হওয়া সত্ত্বেও তিনি মুহূর্তের তরেও বিচলিত হইয়া পড়েন নাই। সময় ও সুযোগ মত শ্রম ও দিন-মজুরী করিয়া জীবিকা সংগ্রহ করিতে তিনি বিন্দুমাত্র সংকোচ বোধ করিতেন না। খলীফার মসনদে আসীন হওয়ার পরও তাঁহার এই কৃচ্ছ্র সাধনায় সামান্য পার্থক্যও সূচিত হইতে পারে নাই। তাঁহার তুচ্ছাতিতুচ্ছ খাবার দেখিয়া লোকেরা স্তম্ভিত ও হতবাক হইয়া যাইত। লোকদের তিনি বলিতেনঃ ‘মুসলমানদের খলীফা রাষ্ট্রীয় বায়তুলমাল হইতে মাত্র দুইটি পাত্র পাইবার অধিকারী। একটিতে নিজে ও নিজের পরিবারবর্গ মিলিয়া খাইবে। আর অপরটি জনগণের সামনে পেশ করিবে’।
তাঁহার ঘরের কাজ সম্পন্ন করার জন্য বাড়তি কোন লোক ছিল না। নবী সম্রাট-তনয়া স্বহস্তেই সমস্ত কাজ সম্পন্ন করিতেন। বৈষয়িক ধন-সম্পদের দিক দিয়া হযরত আলী (রা) শূন্যপাত্র ছিলেন। কিন্তু আত্তার দিক দিয়া তিনি ছিলেন বিপুল সম্পদের অধিকারী। কোন প্রার্থী তাঁহার দুয়ার হইতে খালি হাতে ফিরিয়া যাইতে পারিত না। এমন কি নিজেদের জন্য তৈয়ার করা খাদ্যও তিনি অবলীলাক্রমে ক্ষুধার্ত ভিখারীর হাতে তুলিয়া দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করিতেন না।
--- সমাপ্ত ---
', 'খিলাফতে রাশেদা', '', 'publish', 'closed', 'closed', '', '%e0%a6%96%e0%a6%bf%e0%a6%b2%e0%a6%be%e0%a6%ab%e0%a6%a4%e0%a7%87-%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%b6%e0%a7%87%e0%a6%a6%e0%a6%be', '', '', '2019-10-31 16:10:33', '2019-10-31 10:10:33', '
খিলাফতে রাশেদা
মাওলানা আব্দুর রহীম (র)
স্ক্যান কপি ডাউনলোড
পূর্বকথা
ইসলাম মূলগতভাবে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ রাষ্ট্র-ব্যবস্থা।এই রাষ্ট্র-ব্যবস্থাকে বাস্তবে রূপদান করার সুমহান দায়িত্ব পালন করিয়াছেন খোদ ইসলামেরই মহানবী হযরত মুহাম্মাদ(স)। নবুয়্যতের সুদীর্ঘ তেইশ বৎসরে মানুষের সামষ্টিক জীবন সম্পর্কে যেসব আইন-কানুন ও বিধি-ব্যবস্থা অবতীর্ণ হইয়াছে, উহার সবকিছুকেই তিনি বাস্তবায়িত করিয়াছেন পুরাদস্তুর একটি রাষ্ট্রীয় কাঠামোর আওতায়। শাসন-প্রশাসন, আইন প্রনয়ন, সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষা, বিচার কার্য সম্পাদন,রাষ্ট্রীয় প্রতিরক্ষা বিধান ইত্যাকার প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ কাজই তিনি সম্পাদন করিয়াছেন সেই একই আইন-কানুন ও বিধি-ব্যবস্থার আলোকে। এইভাবে ইসলামি রাষ্ট্র-ব্যবস্থার একটি স্থায়ী বুনিয়াদ তিনি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন নবুয়্যতের তেইশ বৎসরেই।
মহানবী(স)-র তিরোধানের পর সেই স্থায়ী বুনিয়াদের উপরই গড়িয়া উঠিয়াছে ইসলামের আদর্শ রাষ্ট্র- ব্যবস্থা- খিলাফতে রাশেদা। হযরত আবূ বকর,হযরত উমর, হযরত উসমান,হযরত আলী(রা)- মহানবী(স)-র এই চার ঘনিষ্ঠ সহচর পরম যত্নে ও মমতায় বিন্যস্ত ও বিকশিত করিয়া তুলিয়াছেন নবুয়্যতি ধারার এই রাষ্ট্র-ব্যবস্থাকে। শুধু তাহাই নহে,ইহার পরিধিকে তাঁহারা সম্প্রসারিত করিয়াছেন আরব উপদ্বীপের সীমানা অতিক্রম করিয়া গোটা ইরান ও রোমান সাম্রাজ্যর বিশাল অঞ্চল জুড়িয়া। বস্তুতঃ মানব জাতির ইতিহাসে একমাত্র এই রাষ্ট্র-ব্যবস্থাই যে স্বর্ণোজ্জল অধ্যায় রচনা করিতে পারিয়াছে, তাহা অকাট্যরুপে প্রমাণিত হইয়াছে। আধুনিক রাষ্ট্র-বিজ্ঞানীরা যত চমকপ্রদ তন্ত্রমন্ত্রই উদ্ভাবন করিয়া থাকুন না কেন, মানবতার কল্যাণ সাধনে নবুয়্যতী ধারার এই খিলাফতের ন্যায় বিপুল সাফল্য কোন পদ্ধতিই আর অর্জন করিতে পারে নাই, ইহা এক ঐতিহাসিক সত্য।
দুর্ভাগ্যবশতঃনবুয়্যতী ধারার এই খিলাফত দুনিয়ার বুকে টিকিয়া ছিল মাত্র তিরিশ বৎসর। ইহার পরই রাজতন্ত্র ও স্বৈরতন্ত্রের অভিশাপ নামিয়া আসিয়াছে গোটা মুসলিম জাতির উপর। জাহিলিয়াতের অন্ধকার যবনিকা ঢাকিয়া দিয়াছে তাহাদের সোনালি ভবিষ্যৎকে। বর্তমানে উহারই জের চলিতেছে মুসলিম জাহানের দেশে দেশে। তদুপরি সাম্প্রতিককালে ইহার সহিত যুক্ত হইয়াছে পশ্চিমের ইহুদী-খৃস্টানদের উদ্ভাবিত গনতন্ত্র নামক একটি নব্য জাহিলিয়াত। ইহার বিষময় পরিণতি গোটা মুসলিম জাহানকে আজ নিক্ষেপ করিয়াছে রাজনৈতিক সংকটের ঘূর্ণাবর্তে। আধুনিক কালের তন্ত্রমন্ত্রগুলি তাহাদের কোন সমস্যার সমাধান করা তো দূরের কথা, বরং নূতন নূতন সমস্যার জন্ম দিয়া গোটা মুসলিম সমাজকে ব্যাধিগ্রস্ত করিয়া তুলিতেছে।
এই পরিস্থিতিতে আজ মুসলিম সমাজে ইসলামের আদর্শ রাষ্ট্র-ব্যবস্থা-খিলাফতে রাশেদা সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনার প্রয়োজন অত্যন্ত তিব্রতর হইয়া উঠিয়াছে। মুসলমানদের সকল রাজনৈতিক ব্যাধির একমাত্র নিরাময় যে নবুয়্যতী ধারার খিলাফত, অন্ন কোন তন্ত্রমন্ত্র নয়- এ সত্যটি আজ মুসলিম সমাজের নিকট উদ্ভাসিত করিয়া তোলা একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। মহান ইসলামী চিন্তাবিদ ও দার্শনিক হযরত মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম(রহ) এই প্রয়োজনের তাগিদেই “খিলাফতে রাশেদা” নামক বর্তমান গ্রন্থটি রচনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থে তিনি গতানুগতিক ধারায় ইসলামের চারি খলিফার জীবন-বৃতান্তের উপর খুব বেশি আলোকপাত করেন নাই, বরং তাঁহাদের শাসন-প্রশাসনের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য ও অনুকরণীয় দিকগুলিই যথাসম্ভব বিস্তৃতরুপে তুলিয়া ধরার প্রয়াস পাইয়াছেন। এই দিক দিয়া বাংলাভাষার খিলাফতে রাশেদা সম্পর্কে ইহা একখানি অভিনব গ্রন্থ।
১৯৭৫ সন হইতে ১৯৮০ সন পর্যন্ত গ্রন্থটির দুইটি সংস্করন প্রকাশিত হওয়ার পর গ্রন্থকার নিজেই ইহার নানা অংশ ব্যাপকভাবে পরিমার্জন করিয়াছেন। বর্তমান সংস্করণে মুদ্রণ প্রমাদ্গুলির সংশোধন ছাড়াও ইহাতে অনেক প্রাসঙ্গিক তথ্য সংযোজিত হইয়াছে। ইহাতে গ্রন্থটির সৌকর্য আরো বৃদ্ধি পাইয়াছে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস,গ্রন্থটির বর্তমান সংস্করণ বাংলাভাষী পাঠকদের নিকট অধিকতর সমাদৃত হইবে এবং এদেশের দিকভ্রষ্ট জনগণকে সঠিক পথ-নির্দেশ করিতে বিপুল অবদান রাখিবে।
মহান আল্লাহ গ্রন্থকারের এই দ্বীনী খেদমত কবুল করুন এবং ইহার বিনিময়ে তাঁহাকে জান্নাতুল ফেরদৌসে স্থান দিন, ইহাই আমাদের সানুনয় প্রার্থনা।
মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান
চেয়ারম্যান
মওলানা আবদুর রহীম ফাউন্ডেশন
ঢাকা জুলাই,১৯৯৫
শুরু কথা
ইসলামের পুর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা সম্পর্কে ব্যাপক অধ্যয়ন,চিন্তা-গবেষণা-পর্যালোচনা ও গ্রন্থ প্রণয়ন পর্যায়ে উহার বাস্তব রুপ দানের কাজে আত্মনিয়োগ করার প্রেরনা স্বাভাবিকভাবেই আমার মনে জাগিয়া উঠিয়াছিল।বিশেষতঃ রাসূলে কারীম(স) আল্লাহ্ তায়ালার সর্বশেষ নবী ও রাসূল হিসাবে যে আদর্শিক বিধান উপস্থাপন করিয়াছিলেন তাহা নিছক একটি আদর্শবাদেরই ব্যাপার ছিল না বরং তাহা ছিল পূর্ণ মাত্রায় একটি বাস্তব জীবন-ব্যবস্থা ও সমাজ গঠনের সফল কার্যসুচী। তিনি আল্লাহ্ তা’আলার নিকট হইতে যাহা কিছুই পাইয়াছেন, তাহাই তিনি বাস্তবায়িত করিয়াছেন। ইহাই ছিল তাঁহার স্বাভাবিক কর্মধারা। তিনি যখন দুনিয়া হইতে চির বিদায় লইয়া চলিয়া গেলেন, তখন একদিকে তিনি রাখিয়া গেলেন তাঁহার নিজ হস্তে পূর্ণ প্রযত্নে সংকলিত আল্লাহ্র বাণী-কুরআন মজিদ ও তাঁহার আজীবনের সংগ্রাম-সাধনার ফসল একটি রাষ্ট্র ও সমাজ। কুরআন ও সুন্নাত গ্রন্থাকারে আমাদের সামনে চির সমুজ্জ্বল হইয়া আছে,চিরকালই তাহা থাকিবে। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র ও সমাজের সঠিক চিত্রও রহিয়াছে ইতিহাসের পৃষ্ঠায়।তবে বাস্তবে উহার অস্তিত্ব বর্তমানে নাই বলিলেও চলে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও সাধারণভাবে দুনিয়ার সুস্থ বিবেকসম্পন্ন ও সুক্ষ চিন্তাশীল লোকদের নিকট এবং বিশেষভাবে ইসলাম ও রাসূলের প্রতি ইমানদার লোকদের নিকট রাসূলে কারীম(স)-এর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থা বর্তমান কালেও প্রেরনার অন্যতম প্রধান উৎস। ইহা তাঁহাদের নিকট এখনও আদর্শিক লক্ষ্যস্থলে পরিণত হইয়া আছে এবং চিরকালই তাহা থাকিবে,ইহা সন্দেহাতীত কথা।
নবী করীম(স) যে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন,তাঁহার ইন্তেকালের পর হইতে স্বয়ং তাহাঁরই ঘোষণানুযায়ী উহার নূতন নামকরণ করা হইয়াছেঃ “খিলাফতে রাশেদা”। খিলাফতে রাশেদা বাস্তবতঃতাহাই, যাহা আদর্শগতভাবে কুরআন ও সুন্নাহ বিধৃত, রাসূলে করীম(স) নিজে তাঁহার তেইশ বছরের নবুয়্যাতী জীবনে অবিশ্রান্ত সাধনা ও সংগ্রামের ফলে যে রাষ্ট্র ও সমাজ গঠন করিয়া চালাইয়া গিয়াছেন, খিলাফতে রাশেদা উহারই জের-উহারই দ্বিতীয় অধ্যায়। কুরআন ও সুন্নাহ যদি বীজ হয়, তাহা হইলে “ খিলাফতে রাশেদা” উহার শাখা-প্রশাখা, পত্রপল্লব ও ফুলে ফলে সুশোভিত পুর্নাঙ্গ বৃক্ষ। আর রাসূলে করীম(স)-এর আমল হইল এই বৃক্ষের কাণ্ড বিশেষ। এই পর্যায়ে আমি ব্যাপক অধ্যয়ন ও চিন্তা-গবেষণা চালানো এবং ইহার সঠিক চিত্র বাংলা ভাষায় উদ্ভাসিত করিয়া তোলার সিদ্ধান্ত গ্রহন করি- সে আজ বিশ বছর পূর্বের কথা।অতঃপর বিভিন্ন সময় যতটুকু কথা ও যেসব দিক আমার নিকট স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, তখন ততটুকুই প্রবন্ধাকারে লিখিয়া প্রকাশ করিয়াছি।ইহা গ্রন্থরুপে প্রকাশের ব্যবস্থা হওয়ার পরও ইহার পূর্ণতা বিধানের জন্য কয়েকটি দিক সম্পর্কে আমাকে লেখনী চালাইতে হইয়াছে। ফলে “খিলাফতে রাশেদা” এক সঙ্গে ধারাবাহিকভাবে লিখিত কোন গ্রন্থ হয় নাই-হইয়াছে বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন পর্যায়ে লিখিত এবং প্রকাশিত-অপ্রকাশিত রচনাবলীর সমন্বয়। তবু শেষ পর্যন্ত ইহা গ্রন্থাকারে পাঠকদের নিকট পেশ করা সম্ভব হইতেছে দেখিয়া আল্লাহ্ তা’আলার লাখ লাখ শোকর আদায় করিতেছি।
১৯৭৫ সনের জানুয়ারী মাসে এই গ্রন্থখানি সর্বপ্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল।অল্প সময়ের মধ্যে ইহা নিঃশেষ হইয়া যাওয়ার পর ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হয় ১৯৮০ সনের জুলাই মাসে।ইহা আল্লাহ্র অশেষ মেহেরবানী।
আশা করি আমার অন্যান্য গ্রন্থের ন্যায় এই গ্রন্থখানিও বিদগ্ধ সমাজে সমাদৃত হইবে এবং আদর্শবাদের ক্ষেত্রে এক নূতন প্রেরণার সূত্রপাত হইবে।
-মুহাম্মদ আবদুর রহীম
(ক)
রাসূলেকরীম(স) বলিয়াছেনঃ
**********(আরবী)
আমার পরে তোমাদের মধ্যে যাহারাই জীবিত থাকিবে, তাহারা বহু মতবিরোধ দেখিতে পাইবে। এইরুপ অবস্থায় তোমাদের কর্তব্য হইবে আমারই আদর্শ এবং হেদায়েতপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদুনের আদর্শ গ্রহন করা।তোমার উহা শক্তভাবে ধারন করিবে-কিছুতেই ছাড়িয়া দিবে না।(মুসনাদে আহমাদ,তিরমিযি,ইবনে মাযাহ)
(খ)
একটি দীর্ঘ হাদিসে কুদসীতে রাসূলে করীম(স)-এর পরিচয় ও প্রশংসা উল্লেখের পর তাঁহার সাহাবীদের পরিচয় স্বরূপ আল্লাহ্ তা’আলার এই কথাগুলি উদ্ধৃত হইয়াছেঃ
*******(আরবী)
হযরত মুহাম্মাদের উম্মত তাঁহার অন্তর্ধানের পর মহান সত্যর দিকে আহ্বান জানাইবে এবং সত্যদ্বীন সহকারে সুবিচার ও ইনসাফ করিবে। যাহারা তাহাদের সাহায্য করিবে আমি তাহাদিগকে সম্মানিত করিব।যাহারা তাহাদের জন্য দোয়া করিবে আমি তাহাদিগকে সাহায্য দিব। যাহারা তাহাদের বিরুদ্ধতা করিবে কিংবা তাহাদের উপর বিদ্রোহ করিবে, অথবা তাহাদের হাতের কোন জিনিস কাড়িয়া লইতে ইচ্ছা করিবে তাহাদিগকে চরম অকল্যাণ দ্বারা পরিবেষ্টিত করিয়া ফেলিব।প্রথমোক্ত লোকদিগকে তাহাদের নবীগণের উত্তরাধিকারী বানাইব,তাহাদিগকে আল্লাহ্র দিকে আহ্বানদাতা বানাইব। তাহারা সত্য ও ন্যায়ের আদেশ করিবে এবং অন্যায় ও মিথ্যা হইতে নিষেধ করিবে। তাহারা নামায কায়েম করিবে,যাকাত আদায় করিবে,ওয়াদা পূর্ণ করিবে আমি তাহাদেরপ্রথম পর্যায়ের লোকদের দ্বারা যে কল্যাণের সূচনা করিয়াছি, তাহাদের দ্বারাই সেই কল্যাণকে পরিসমাপ্ত করিব। ইহা একান্তভাবে আমারই অনুগ্রহের ব্যাপার। যাহাকে ইচ্ছা আমি তাহাকেই এই অনুগ্রহ দেই। আর প্রকৃতপক্ষে আমি মহান অনুগ্রহকারী।(ইবনে আবু হাতিম-অহব ইবনে মুনাব্বাহ হইতে ইবনে কাসীর-তাঁহার তাফসীরে।)
ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা
বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ(স) আল্লাহ্ তা’আলার সর্বশেষ নবী ও রাসূল হিসাবে দুনিয়ায় প্রেরিত হইয়াছিলেন। দুনিয়ায় তাঁহার উপর যে দায়িত্ব অর্পিত হইয়াছিল,ইসলামী পরিভাষায় সেই দায়িত্তের সরূপকে এক কথায় বলা যায়ঃ “ইক্কামতে দ্বীন”। আল্লাহ্র দ্বীন পুর্নাঙ্গরুপে কায়েম করাই ছিল সর্বশেষ নবীর মৌলিক দায়িত্ব। এই বাক্য হইতে স্বতঃই স্পষ্ট হইয়া উঠে যে, তিনি “দ্বীন” নিজে রচনা করেন নাই, আল্লাহ্র নিকট হইতে গ্রহন করিয়াছেন। এই “দ্বীন”অহীর মাধ্যমেই তাঁহার প্রতি আল্লাহ্র নিকট হইতে নাজিল হইয়াছে। এই হিসাবে তিনি আল্লাহ্র রাসূল। আল্লাহ্র নিকট হইতে পাওয়া “অহী” মৌলিক প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে উহার যথাযথ ব্যাখ্যা দান এবং নিজের জীবনে বাস্তব অনুসরণের মাধ্যমে উহাকে সমুদ্ভাসিত করিয়া তোলাও ছিল নবী-রাসূল হিসাবেই তাঁহার দায়িত্তের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু “ইক্কামতে দ্বীন”-এর জন্য এইটুকু কাজই যথেষ্ট ছিলনা,আল্লাহ্র নাজিল করা আইন-বিধানকে ব্যক্তি জীবনে ও সমাজ-সমষ্ঠির সার্বিক ক্ষেত্রে পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত করাও ছিল নবী-রাসূল হিসাবেই তাঁহার কর্তব্য। এই কারণে তাঁহাকে যে দ্বীনী দাওয়াতী প্রচেষ্টা চালাইতে হইয়াছে, তাহাই বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করিয়া একটি পুর্নাঙ্গ রাষ্ট্ররূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। এই হিসেবে তিনি ইসলামী রাষ্ট্রের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা এবং উহার জনগণের একচ্ছত্র নেতা ও রাষ্ট্রপ্রধান।
আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে রাষ্ট্র বলিতে যাহা বুঝায়,নবী করীম (স)-এর সাধনা-সংগ্রামের পরিণতিতে সেই জিনিসেরই পূর্ণ প্রতিফলন বিদ্যমান।“রাষ্ট্র” একটি রাজনৈতিক সংস্থা। মানব জীবনের প্রয়োজন পরিপূরণের উদ্দেশ্য এই সংস্থাটি গড়িয়া তোলা হয় এবং জীবনকে কল্যাণময় ও উন্নততর করিয়া তোলার জন্য ইহার অস্তিত্ব অক্ষুন্ন ও স্থায়ী করিয়া রাখা হয়।“রাষ্ট্র”মানব-শক্তির উন্নততর ফসল। যেখানে মানব জাতির একটা বিরাট সংখ্যা-সমষ্ঠি সাধারনতঃএকটা নির্দিষ্ট ভৌগলিক অঞ্চলের দখলদার এবং বহু সংখ্যক লোকের একটা নির্দিষ্ট সংখ্যক শ্রেণীর ইচ্ছা তাহাদের সম্মিলিত শক্তির কারণে উহার বিরুদ্ধবাদীদের দমন-উদ্দেশ্য কার্যকর হইতে পারে; সেখানেই রাষ্ট্র অস্তিত্বশীল। আর সংক্ষিপ্ত ভাষায়, কোন বিশেষ ভূ-খণ্ডের রাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে গড়িয়া উঠা জাতীয় সত্তাকেই বলা হয় রাষ্ট্র বা State।
রাষ্ট্রবিজ্ঞান প্রদত্ত এই সংজ্ঞাসমূহ হইতে নিম্নোক্ত চারটি জিনিসই রাষ্ট্রের মৌল উপকরণ রূপে প্রমাণিত হইয়াছেঃ(১)জনতা(population),(২)নির্দিষ্ট ভূখন্ড(Territory),(৩)সার্বভৌমত্ব(Sovereignty)এবং (৪)প্রশাসন যন্ত্র বা সরকার(Government)।
রাসূলে করীম(স)-এর মদীনায় উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত তাঁহার দায়িত্ব পালন প্রচেষ্টার যে ফসল ফলিয়ছিল, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে সুক্ষাতিসুক্ষ বিচার-বিবেচনায়ও তাহাতে এই চারটি মৌল উপকরণ পূর্ণমাত্রায় বর্তমান ছিল-যদিও দৃষ্টিকোণ ও মৌল ভাবধারার দিক দিয়া উহার স্বরূপ ছিল অন্যান্য সব রাষ্ট্রবিজ্ঞান হইতে সম্পূর্ণ ভিন্নতর।
রাষ্ট্রের প্রথম ভিত্তিস্থাপন
নবী করীম(স) আল্লাহ্র রাসূল ও নবীরুপে মনোনীত হওয়ার পর দ্বীন-ইসলামের যে বিপ্লবাত্মক আদর্শ প্রথমে গোপনে এবং পরে প্রকাশ্য প্রচার করিতে শুরু করিয়াছিলেন, তাহাতে তদানীন্তন কুরাইশদের ধর্মমত, নৈতিক চরিত্র, অর্থ ব্যবস্থা এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে প্রবল প্রতিক্রিয়া সূচিত হইয়া ছিল। সত্য কথা এই যে, ইহার দরুণ তাহাদের সর্ব প্রকার স্বার্থ ও আশা-আকাঙ্খা এক কঠিন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হইয়া পড়িয়াছিল। এই কারণে কুরাইশরা নবী করীম(স) এবং তাঁহার প্রতি ইমানদার মুসলমানদের জীবনকে দুঃসহ অত্যাচার ও নিপীড়নে জর্জরিত করিয়া তুলিয়াছিল। শেষ পর্যন্ত তিনি আল্লাহ্ তা’আয়ালার নির্দেশানুক্রমে মক্কা ত্যাগ করিয়া মদিনায় চলিয়া যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহন করেন। এই সময় নবী করীম(স) হজ্জ উদযাপন উদ্দেশ্য আগত মদিনার মুসলমানদের নিকট হইতে দুই-দুইবার আনুগত্যর “বায়’আত”১ {শব্দটির ব্যবহারিক ও পারিভাষিক অর্থ “আনুগত্যর শপথ”।} ইতিহাসে এই “বায়আত”দুইটি “প্রথম আকাবা-বায়’আত”ও “দ্বিতীয় আকাবা-বায়’আত”২{‘আকাবা’ বায়’আতের পূর্ণ বিবরণ এইরূপঃ মদীনার লোকেরা রাত্রির তৃতীয় প্রহরে ‘আকাবা’ নামক স্থানে সমবেত হইয়া রাসূলে করীম(স)-এর আগমন প্রতীক্ষায় উদগ্রীব। একটু পরেই নবী করীম(স) তাঁহার চাচা আব্বাসকে(তিনি তখন ইসলাম গ্রহন করেন নাই)সঙ্গে লইয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন।প্রথমেই আব্বাস বলিলেনঃ হে খাজরাজ গোত্রের লোকের! তোমরা ভাল করিয়াই জান, মুহাম্মদ (স) আমাদের মধ্যে অত্যন্ত সম্মানিত ও মর্যাদাবান ব্যক্তি। তাঁহার শত্রুদের হইতে আমারাই তাঁহার সংরক্ষক। কিন্তু এক্ষণে তিনি নিজেই এই শহর(মক্কা) ত্যাগ করিয়া তোমাদের সহিত মিলিত হওয়ার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কেননা তোমরা তাঁহাকে নিজেদের শহরে আহ্বান জানাইতেছ। তোমরা যদি তাঁহার পূর্ণ সংরক্ষনে শক্তিশালী হইয়া থাক এবং তাঁহার শত্রুদের হাত হইতে তাঁহাকে রক্ষা করার সাহস তোমাদের থাকে, তাহা হইলে তোমরা ইহা কর। অন্যথায় এখনি তোমাদের ‘না’ বলিয়া দেওয়া উচিৎ। কেননা মুহাম্মাদ এখন তো আমাদের হেফাজতে আছেন। তোমরা তাঁহাকে লইয়া গিয়া শত্রুদের হাতে ছাড়িয়া দিবে- এমনটি যেন না হয়। তাঁহারা বলিলেন, ‘আমরা আপনার কথা শুনিয়াছি। এখন সে রাসূল, আপনার বক্তব্য বলুন। আল্লাহ্র বিধান কিংবা আপনার নিজের সম্পর্কে আমাদের নিকট হইতে যদি কোন প্রতিশ্রুতি লইতে হয়, তবে তাহা গ্রহন করুন। ইহার পর নবী করীম(স) প্রথমে কুরআন মজিদের অংশ বিশেষ পাঠ করিলেন। আল্লাহ্র বন্দেগী কবুল করার এবং তাঁহার সহিত শিরক না করার শর্ত পেশ করিলেন। অতঃপর বলিলেনঃ ‘আমি তোমাদের নিকট হইতে প্রতিশ্রুতি লইতেছি যে, তোমরা আমার সাহায্য সহযোগিতা ও সমর্থন এমনভাবে করিবে,যেমন তোমরা তোমাদের স্ত্রীলোকদের ও তোমাদের সন্তানদের করিয়া থাক’। ইহার সঙ্গে সঙ্গে রাসূলে করীম(স)-এর হাত ধরিয়া তাঁহারা বলিয়া উঠলেনঃ ‘হ্যাঁ,সেই মহান সত্তার শপথ,যিনি আপনাকে সত্য-সঠিক দ্বীনসহ পাঠাইয়াছেন,আমরা এমনিভাবেই আপনার সহায়তা ও সংরক্ষণ করিব, যেমন আমরা আমাদের পরিবারবর্গের করিয়া থাকি’। অতঃপর সকলেই সমবেতভাবে বলিলেনঃ ‘আমরা প্রতিশ্রুতি দিতেছি, আমরা সর্বাবস্থায় আপনার কথা শুনিব, আপনার আনুগত্য স্বীকার করিব- দুঃখ-বিপদ,স্বাচ্ছন্দ্য-সচ্ছলতা কিংবা অভাব-অনটন যাহাই হউক না কেন আর আমরা যেখানেই থাকি না কেন, আমরা সর্বসময় ও সর্বাবস্থায় সত্য বলিব;কাহাকেও ভয় করিব না এবং কোন উৎপীড়নেরও পরোয়া করিব না।
অতঃপর তাঁহার বলিলেনঃ ‘আমাদের মনে একটা প্রশ্ন জাগিতেছে। এমন তো হইবে না যে, আল্লাহ্ তা’আলা যখন আপনাকে বিজয় দান করিবেন,তখন আপনি আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া আপনার নিজের জাতির লোকদের সহিত মিলিত হইয়া যাইবেন’? ইহা শুনিয়া নবী (স) স্মিত হাসি হাসিলেন এবং বলিলেনঃ
*******(আরবী)
না,এ বিষয়ে তোমরা নিশ্চিন্ত থাক। তোমরা যাহার সহিত লড়াই করিবে,আমিও তাহাদের সহিত লড়াই করিব। তোমরা যাহাদের সহিত সন্ধি করিবে আমিও তাহাদের সহিত সন্ধি করিব। তোমাদের দায়িত্ব আমার দায়িত্ব। তোমাদের মর্যাদা-সম্ভ্রম আমার মর্যাদা ও সম্ভ্রম রুপে গণ্য হইবে। আর আমার জীবন ও মরন তোমাদের সঙ্গেই হইবে।
বস্তুতঃ আকাবায় এইরুপ কথোপকথনের মাধ্যমে প্রকারান্তরে একটি সামাজিক-সামষ্ঠিক চুক্তিই সম্পাদিত হইয়াছিল। ইহার মাধ্যমে মদিনাবাসীরা রাসূলে করীম(স)-কে নিজেদের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতা এবং রাষ্ট্র-কর্তারুপে যুগপৎ মানিয়া লইলেন এবং তাঁহাদের আহ্বানে তিনি মদীনায় চলিয়া গেলেন। নবী করীম(স) হইলেন তাঁহাদের একচ্ছত্র নেতা।}নামে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। এই সময় দুইজন স্ত্রীলোকসহ মদিনার আওস ও খাজরাজ নামক দুই প্রধান বিবাদমান গোত্রের মোট প্রায় ৭৫জন মুসলমান ঐক্যবদ্ধ হইয়া রাসূলে করীম(স)-এর হাতে ‘বায়’আত’ গ্রহন করেন। এই বায়’আতে তাঁহারা দ্বীন- ইসলামকে পুর্নাঙ্গভাবে মানিয়া ও অনুসরণ করিয়া চলার সঙ্গে সঙ্গে নবী করীম(স)-এর সার্বিক নেতৃত্ব মানিয়া লওয়ার,তাঁহার জন্য পূর্ণ নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহন করার এবং তাঁহার নেতৃত্বে বিরুদ্ধ পক্ষের সহিত প্রাণ-পণ যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হওয়ার অঙ্গীকার দান করেন। শুধু তাহাই নয়, নবী করীম(স)-কে তাঁহার সঙ্গী-সাথীসহ মদীনায় যাইবার জন্য তাঁহারা আহ্বান জানান এবং সেখানে তাঁহাদিগকে বসবাসের জন্য স্থান দেওয়ার প্রতিশ্রুতিরও পুনরুল্লেখ করেন। মদীনাবাসীরা নবী করীম(স)-কে একজন ‘আশ্রয় গ্রহণকারী’(Settler-Asylum) রুপে নয়-আল্লাহ্র রাসূল ও প্রতিনিধি এবং তাঁহাদের সর্বাত্মক নেতা ও প্রশাসক হিসেবেই এই আহ্বান জানাইয়াছিলেন। নবী করীম(স) এই আহ্বান গ্রহন করিয়া সঙ্গিসাথী সমভিব্যহারে মদিনায় স্থানান্তরিত হওয়ার সিদ্ধান্ত ও এইখানে ঘোষণা করেন। বস্তুতঃ একটি রাষ্ট্রের দানা বাঁধিয়া উঠার মূলে সর্বপ্রথম যে সামাজিক-সামষ্ঠিক চুক্তি(Social Contract)-র অবস্থিতি প্রথম শর্ত, মদীনায় প্রতিনিধি স্থানীয় অধিবাসীদের নিকট হইতে নবী করীম(স)-এর গৃহীত আকাবার এই ‘বায়াআত’ সেই চুক্তিরই বাস্তব রূপ। প্রকৃতপক্ষে এই ‘বায়’আতে’র মাধ্যমেই ইসলামী রাষ্ট্রের প্রথম ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছিল। এই ‘বায়’আত’ মক্কার এক নির্জন পর্বতগুহায় অনুষ্ঠিত হইলেও উহার জন্য স্থান(Territory)নির্দিষ্ট হইয়াছিল মদীনা। ‘মদীনা’ এই সময় হইতেই ‘মদীনাতুর-রাসূল’- রাসূলের মদীনা কিংবা ‘মদীনাতুল-ইসলাম’- ইসলামের কেন্দ্রভূমি মদীনা-নামে অভিহিত হইতে শুরু করিয়াছিল।পাশ্চাত্য রাষ্ট্রবিজ্ঞানে একটি রাষ্ট্র(State)-এর সর্বশেষ সংজ্ঞায় যে কয়টি জরুরী শর্ত উল্লেখিত হইয়াছে,সেই সব কয়টিই এখানে পুরাপুরি বর্তমান মদিনার মুসলমানগণ যে ‘বায়আত’ করিয়াছিলেন এবং এই প্রসঙ্গে উভয় পক্ষে যে কথোপকথন হইয়াছিল, তাহা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, নবী করীম (স)-কে তাঁহারা মদীনা গমনের আহ্বান জানাইয়া এক কঠিন বিপদের ঝুঁকি মাথায় লইয়াছিলেন।তাঁহারা ইহা অবলীলাক্রমে সহ্য করিয়া যাইতে সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত ছিলেন। অন্যকথায়, একটি ক্ষুদ্রায়তন উপশহর যেন নিজেকে নিজে সমগ্র দেশের চূরান্ত শত্রুতা এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক বয়কটের মুখে ঠেলিয়া দিতেছিল। অবশ্য ইহার পরিনতিও ঠিক তাহাই হইয়াছিল।
অপরদিকে মক্কাবাসীদের জন্য ও এই বায়’আত বিশেষ অর্থবহ এবং বিপজ্জনক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। কেননা মুসলমানগণ মক্কার বাহিরে অন্য একস্থানে একত্রিত হইলেও- ইহারই মাধ্যমে একটি শক্তি, একটি রাষ্ট্ররূপে এবং মক্কাবাসীদের কুফর-শিরক, অরাজকতা-উচ্ছৃঙ্খলতার প্রতি একটা মারাত্মক চ্যালেঞ্জ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। অর্থাৎ মক্কাবাসীদের জন্য ইহা শুধু ধর্মীয় বিপদই নয়, ইহা একটি সুস্পষ্ট ‘রাজনৈতিক বিপদ’ হইয়া দেখা দিয়াছিল। মদিনা যেহেতু ইয়ামেন হইয়া সিরীয়া যাওয়ার বাণিজ্য পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান সেহেতু এখানে মুসলমানদের রাষ্ট্ররূপে পরিগ্রহের ফলে এই পথটি তাহাদের জন্য চিরতরে বন্ধ হইয়া যাইবার কিংবা অন্ততঃবিপদ-সঙ্কুল হইয়া পড়ার আশংকা দেখা দিয়াছিল। অথচ এই পথটি ছিল কুরাইশ ও অনন্যা বড় বড় গোত্রের লোকদের অর্থনৈতিক জীবনের প্রধান যোগসূত্র। কুরাইশরা ইহার পরিণতি মর্মে মর্মে অনুধাবন করিতে পারিয়াছিল। সে কারণে তাহারা বিশ্বনবীর জীবন-প্রদীপ চিরতরে নির্বাপিত করিয়া ফেলার জন্য পূর্বাহ্ণেই ঐক্যবদ্ধভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহন করিয়াছিল।
এক কথায়, এই ‘বায়’আত’ একদিকে যেমন ছিল প্রথম ইসলামী রাষ্ট্র-সংস্থার ভিত্তিপ্রস্তর, অপরদিকে ইহার মাধ্যমে একটি আদর্শিক সমাজ-সংস্থার ভিত্তিও সংস্থাপিত হইয়াছিল। বস্তুতঃ জানা ইতিহাসে(Known History) পুরাপুরি আদর্শ-ভিত্তিক রাষ্ট্র বলিতে এইটিকেই বুঝায়।
মদিনায় ইসলামী রাষ্ট্র
আকাবার বায়’আত অনুসারে রাসূলে করীম(স)-এর হিজরাতের সঙ্গে সঙ্গে ইসলাম মদীনায় স্থানান্তরিত হইল। প্রথমে যাহা ছিল বীজ, এক্ষণে তাহাই হইল বৃক্ষ। যাহা ছিল থিওরী(Theory),এক্ষণে তাহাই হইল বাস্তব(Practical)। প্রথম যাহা ছিল নিছক মৌখিক আনুগত্যর মধ্যে সীমাবদ্ধ, এক্ষণে তাহাই দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডে ও সামাজিক-সামষ্ঠিক বিষয়াদিতে অনুসৃত হইয়া শরীরী হইয়া উঠিল। মক্কায় যাহা ছিল সূচনা, মদীনায় তাহাই অগ্রগতির স্তরসমূহ অতিক্রম করিয়া ধাপে ধাপে পুর্নত্তের দিকে আগাইয়া যাইতে লাগিল।
মদীনায় পৌছিয়া নবী করীম(স) প্রথম পর্যায়েই দুইটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করিলেন। প্রথম কাজটি হইল, একটি মসজিদের ভিত্তিস্থাপন। এই মসজিদ কেবল পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ার স্থানই নয়, ইহা মুসলিম জনতার মিলন-কেন্দ্রে পরিণত হইল। এই স্থানকে কেন্দ্র করিয়াই নবী করীম(স) ইসলামের জন্য আত্মোৎসর্গীকৃত লোকদের লইয়া একটি আদর্শ-ভিত্তিক সামাজিক-সামষ্ঠিক শক্তির লালন ও বিকাশ সাধনের জন্য প্রচেষ্টা চালাইয়া যাইতে শুরু করিলেন। তিনি ইসলামের মহান আদর্শের ভিত্তিতে একটি পুর্নাঙ্গ রাষ্ট্র পরিচালনের যোগ্য নাগরিক ও কর্মী-নেতৃবাহিনী গড়িয়া তোলার সর্বাত্মক সাধনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন এই মসজিদকে কেন্দ্র করিয়া। এই মসজিদই ছিল রাষ্ট্রপ্রধান ভবন,সেনাধ্যক্ষর(Supreme Commander) হেড কোয়ার্টার এবং সর্বোচ্চ প্রশাসকের কেন্দ্রীয় অফিস।
দ্বিতীয় কাজ হইল, মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে পারস্পরিক ভ্রাতৃসম্পর্ক স্থাপন। ইহা ছিল কুরআনের সুস্পষ্ট নির্দেশের বাস্তব অনুসরণ। নির্দেশটি এইঃ
*******(আরবী)
মু’মিন লোকেরা পরস্পরের ভাই; অতএব তোমরা এই ভাইদের মধ্যে পারস্পরিক সন্ধি ও কল্যাণ স্থাপন কর। আর সকলে সম্মিলিতভাবে আল্লাহ্কে ভয় করিয়া চল; তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করা হইবে বলিয়া আশা করা যায়।
ইসলাম সমগ্র বিশমানবতার অভিন্ন ভ্রাতৃত্বের পয়গাম লইয়া আসা গতিশীল ও যুগোপযোগী এক মহান বিধান। বর্ণিত ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়া রাসূলে করীম(স) সেই বিরাট বিশ্বমানবিকতারই ভিত্তি স্থাপন ও কর্ম-ধারার সূচনা করিয়াছিলেন।ইহার মাধ্যমে তিনি স্থান-কাল-ভূগলের সীমা ও ভাষার পার্থক্য এবং বংশ-রক্ত-গোত্রের বিভেদ সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করিয়া দিলেন। এই ভ্রাতৃ-সম্পর্কের কারণে স্থানীয় ও অস্থানীয় ভেদাভেদো চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। সমস্ত বৈষয়িক-বস্তুগত পার্থক্য-বিভেদ নিঃশেষ করিয়া দিয়া নবী করীম (স) এক সার্বজনীন ভ্রাতৃত্বের সমাজ(Society of Universal Brotherhood) গড়িয়া তুলিতে শুরু করিয়াছিলেন।
এই ভ্রাতৃপ্রতীম সমাজের ভাবধারা ছিল এই যে, এখানে কেউ ছোট নয়, কেউ বড় নয়। কেউ হীন নয়, কেউ মানী হয়। কেউ আশরাফ নয়, কেউ আতরাফ নয়। কেউ কুলীন নয়, কেউ অকুলীন নয়। এই সমাজের প্রতিটি মানুষ ইসলামের মহান আদর্শে সমান মর্যাদা ও অধিকারসম্পন্ন ভাই মাত্র। ‘মুসলমান’ ই ইহাদের একমাত্র পরিচয়। ইহা ছাড়া তাহাদের আর কোন পরিচয় নাই।
দ্বিতীয় পর্যায়ে এই ভ্রাতৃত্ববোধক নবী করীম(স) সমাজ পুনর্গঠনের ও পুনর্বাসনের একটি কার্যকর হাতিয়ারে পরিণত করেন। তাহার গঠিত এই সমাজের প্রত্যেক ভাই তাহার অপর ভাইয়ের জন্য প্রয়োজনীয় সর্ব প্রকার ত্যাগ স্বীকার করিতে সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত। যাহার আছে সে সেই সব কিছুই দিবে তাহাকে,যাহার সেইসব নাই। কিন্তু ইহা ‘দান’ হইবেনা-হইবেনা ‘অনুগ্রহ’।গ্রহীতা তাহা গ্রহন করিয়া দাতার প্রতি হইবেনা অনুগ্রহীত,করুণার পাত্র-লাঞ্ছিত ও অবমানিত। ইহা তাহার কর্তব্য। একজন তাহার ভাইকে কিছু দিবে, দেওয়া তাহার কর্তব্য বলিয়া। ভাই তাহা গ্রহন করিবে তাহার ভাইয়ের কর্তব্য পালনে সহযোগিতা করার মানসিকতা লইয়া। ইহারই পরিণতিতে কল্পনাতীত স্বল্প সময়ে মক্কা হইতে নিঃস্ব সর্বস্বান্ত হইয়া আসা বিপুল সংখ্যক লোকের পুনর্বাসনের কঠিন ও জটিল সমস্যার অনায়াসে সমাধান হইয়াছিল। শুধু তাহাই নয়, সামগ্রিকভাবে নব প্রতিষ্ঠিত ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র বিপুল সচ্ছলতায় সমৃদ্ধ এবং নূতন শক্তিতে বলিয়ান হইয়া উঠিয়াছিল। প্রতিটি নাগরিকই নিজের উপার্জনের প্রেরণা ও সুযোগ লাভ করিল। ফলে কেহ কাহারও উপর ‘বোঝা’ বা নির্ভরশীল(Dependent) হইয়া থাকিল না।
তৃতীয় পর্যায়ে বিশ্লিষ্টটা ও বিশৃঙ্খলার বুক হইতে ঐক্য, সংহতি ও শৃঙ্খলা গড়িয়া তোলার কঠিন দায়িত্ব রাসূলে করীম (স)-এর সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিল। কার্যতঃ ইহা ছিল একটা পর্বততুল্য বিরাট সমস্যা। অতিতের নবি-রাসূলগণ ও এই সমস্যাটির সমাধানে সফল হইতে পারেন নাই। কিন্তু রাসূলে করীম(স)-কে তাহাই করিতে হইয়াছে এবং তিনি তাহা করিয়াছেন অপূর্ব সাফল্য ও যোগ্যতা সহকারে। দৌর্বল্য,অক্ষমতা ও শক্তিহীনতা বুক দীর্ণ করিয়া শক্তি ও সামর্থের বিরাট বৃক্ষ গড়িয়া তোলাই ছিল তাঁহার সাধনা। পারস্পরিক বিরোধ ও বৈষম্য দূরীভূত করিয়া নিঃছিদ্র একত্বটা ও ঐক্যবদ্ধটা সৃষ্টি করাই ছিল তাঁহার লক্ষ্য। মৃত্যুর তুহীন হিম অপসারিত করিয়া জীবনের উষ্ণতা,চাঞ্চল্য ও তৎপরতা নূতন জগত নির্মাণই ছিল তাহার কর্তব্য। আল্লাহ্ তা’য়ালা এই দিকে ইংগিত করিয়াই বলিয়াছেনঃ
********(আরবী)
এবং আমরা আপনার সেই দুর্বহ বোঝাটি আপনার উপর হইতে নামাইয়া দিলাম,যাহা আপনার পৃষ্ঠদেশ নিচু করিয়া দিয়াছিল।
চতুর্থ পর্যায়ে তাঁহার কর্তব্য ছিল ‘বাহির সামলানো’। এ পর্যন্ত তিনি যাহা কিছু করিয়াছেন তাহাকে বলা চলে ঘর সামলানোর কাজ। কিন্তু কেবল ঘর সামলাইলেই দায়িত্ব পালন সম্পূর্ণ হয় না।ইসলামী সমাজের আভ্যন্তরীণ ঐক্য ও নিরাপত্তা বিধানের পর উহাকে স্থায়ীভাবে সংরক্ষিত করার জন্য দুই পর্যায়ের কাজ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিল। একটি ছিল,ঘরের সংলগ্ন পরিমণ্ডলে অবস্থানকারী অমুসলিম ইয়াহুদি সমাজের নিত্য-নৈমিত্তিক-তথা প্রতি মুহূর্তের শত্রুতার আক্রমন হইতে ইসলামী সমাজের নিরাপত্তা বিধান। আর দ্বিতীয় কাজটি হইল, বহিঃশত্রুর সর্বাত্মক আক্রমণ হইতে ইসলামী রাষ্ট্রের এই নব নির্মিত প্রাসাদটির পুর্নাঙ্গ সংস্করণের সুষ্ঠু ও নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহন আর সেই সঙ্গে সমগ্র বিশ্বে ইসলামের ব্যাপক প্রচারের রাজপথ উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া।
তখনকার মদীনা শহরে এক প্রকার নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা অবস্থা বিরাজ করিতেছিল।সেখানকার আওস ও খাজরাজ এই দুইটি বড় ও প্রধান গোত্র প্রায় চারটি খণ্ডে বিভক্ত ছিল। অপর দিকে ইয়াহুদিদের দশটি গোত্র ছিল তাহাদের হইতে স্বতন্ত্র। শতশত বৎসরের শত্রুতা তাহাদিগকে পরস্পরের প্রানের দুশমন বানাইয়া দিয়াছিল।সাধারনতঃ কয়েকটি আরব গোত্র তাহাদের শত্রুদের সঙ্গে লড়াই করার উদ্দেশ্য ইয়াহুদিদের সহায়তা আদায় করিয়া লইত। অপর কতিপয় আরব গোত্র অন্য কয়েকটি বিরোধী গোত্রের সাহায্য লাভ করিত। অতঃপর যে রক্তাক্ত যুদ্ধ শুরু হইয়া যাইত,তাহা বংশানুক্রমে ও শতাব্দীকাল ধরিয়া অব্যাহত থাকিত। ইহার ফলে আরবের সাধারণ মানুষের জীবনে চরম দুঃখ ও কষ্ট নামিয়া আসিত। তাহারা এই প্রাণান্তকর অবস্থা হইতে মুক্তি লাভের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা চালাইতেছিল। এই জন্য নবী করীম(স)-এর মদীনা আগমনের প্রাক্কালে মদীনাবাসীদের একটা বিরাট অংশ আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সলুলকে নিজেদের বাদশাহ ও শাসক নিযুক্ত করার সিদ্ধান্ত লইয়াছিল। নবী করীম(স) মদীনার জনগনের এই অবস্থা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। এই অবস্থার পরিবর্তনের জন্য তিনি আকাবা বায়আত গ্রহনের পরই মদীনার বিভিন্ন গোত্রের বারো জন সদস্যকে ‘নকীব’ নিযুক্ত করিয়াছিলেন এবং এইভাবে তিনি পারস্পরিক সংঘর্ষলিপ্ত ও বিবাদমান গোত্রগুলির মধ্যে একটা মিলমিশ ও ঐক্য সৃষ্টির জন্য চেষ্টা চালাইয়াছিলেন। কিন্তু এই গোত্রবাদী সমাজের প্রতিটি গোত্রই ছিল সম্পূর্ণ স্বাধীন,স্ব-ব্যবস্থাপনার(Self-administration) অধিকারী এবং নিজেদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বেচ্ছানুবর্তী।এতদ্ব্যতীত সেখানে এই গোত্রসমূহকে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত ও ঐক্যবদ্ধ রাখিবার কোন প্রশাসন-ব্যবস্থা বা কার্যকর প্রতিষ্ঠান(Executive Institution)-ই ছিলনা। এতৎসত্ত্বেও নবী করীম(স) প্রেরিত ইসলাম প্রচারকদের চেষ্টায় মদীনাবাসীদের মধ্য হইতে বহু সংখ্যক লোক ইসলাম গ্রহন করিয়া মুসলিম সমাজের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল,যদিও তখন পর্যন্ত মদীনায় ইসলাম কোন রাজনৈতিক শক্তির মর্যাদা লাভ করিতে পারে নাই।
নবী করীম (স) মদীনায় উপস্থিত হইয়া এই অরাজক পরিস্থিতির অবসান ঘটাইবার উদ্দেশ্য একটি ঘোষণাপত্র তৈয়ার করিলেন।১ {ইতিহাসে এই ঘোষণাই ‘মদিনা-সনদ’ নামে বিধৃত।} এই ঘোষণায় মদীনা একটি ‘নগর রাষ্ট্রের’(city state) মর্যাদা পাইল। উহার ভিত্তিতে সমগ্র বিচ্ছিন্ন দো বিক্ষিপ্ত গোত্রসমূহের মধ্যে বিশেষভাবে ঐক্য ও সংহতি সৃষ্টির জন্য যারপরনাই চেষ্টা করা হইল।
একথা সর্বজনবিদিত যে, এই লোকেরা অতিতে কখনই কোন রাষ্ট্রশক্তির(State-power/coercive power)নিকট মাথা নত করে নাই। কোন দিনই তাহারা কেন্দ্রীয় শক্তির নিয়ম-শৃঙ্খলা ও প্রভুত্বের অধীনতা পাশে আবদ্ধ ছিল না। নবী করীম(স) এই ঘোষণাপত্রের সাহায্যে তাহাদের সকলকে একটি আইন, তথা এক আল্লাহ্, এক নেতৃত্ব ও একই কিবলার উপর সুসংবদ্ধ ও সুসংহত করিয়া দিলেন। ব্যক্তিগত অধিকারের দিক দিয়া মদীনা-ঘোষণা(Medina Diclaration) ছিল একটি বিপ্লবাত্মক পদক্ষেপ। পূর্বে যে অধিকার এক ব্যক্তি বা একটি পরিবার কিংবা একটি গোত্র ভোগ করিত, এই ঘোষণা কার্যকর হওয়ার পর তাহা সর্বসাধারণের অধিকার রূপে সাব্যস্ত হইল। এইভাবে একদিকে গোত্রবাদমূলক নৈরাজ্যের অবসান ঘটিল এবং অপরদিকে সঠিক অর্থে ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপিত হইল।
মদীনা-চুক্তি(Medina Pact)-র ধারা অনুযায়ী সমগ্র প্রশাসনিক(Administrative),আইনগত(Legal)ও ফৌজদারি বা বিচার বিভাগীয়(Judicial) ক্ষমতা হযরত মুহাম্মাদ(স)-এর উপর অর্পিত হইয়াছিল। তবে এই ব্যাপারে বিশ্বনবী ও দুনিয়ার অন্যান্য শাসকদের মধ্যে বিরাট পার্থক্য বিদ্যমান। তিনি কোন স্বেচ্ছাচারী ও দুর্বিনীত শাসক রূপে এই ব্যাপক ও সর্বময় ক্ষমতা গ্রহন করেন নাই। কোনরূপে ব্যক্তি স্বার্থ,ব্যক্তি সার্বভৌমত্ব ও ব্যক্তি আধিপত্যের একবিন্দু ধারণাও তাঁহার সম্পর্কে করা যাইতে পারেনা;বরং তাঁহার রাষ্ট্রনীতি উন্নত নৈতিক ও মানবিক আদর্শের উপর ভিত্তিশীল ছিল। তিনি নিজেকে একজন সার্বভৌম(Sovereign) হিসাবে এক মুহূর্তের তরেও চিন্তা করেন নাই, জনসমক্ষে সেভাবে নিজেকে পেশও করেন নাই। যে আইন তিনি অন্যদের উপর প্রয়োগ করিতেন, তাহা অন্যদের ন্যায় নিজের উপরও প্রয়োগযোগ্য মনে করিতেন। বস্তুত দুনিয়ার রাষ্ট্রীয় ইতিহাসে ইহার কোন দৃষ্টান্ত দেখানো যাইতে পারে না।
মদীনা-চুক্তি দুইটি অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশ ২৩টি ধারা সমন্বিত।উহা সম্পূর্ণ মুহাজির ও আনসারদের সহিত সংশ্লিষ্ট। আর দ্বিতীয় অংশ মদীনার ইয়াহুদীদের অধিকার ও কর্তব্য-দায়িত্ব সম্পর্কিত।
এই চুক্তি অনুযায়ী সমাজ ও রাষ্ট্রের সর্ব ব্যাপারে নবী করিম (স)-এর ফয়সালা ও রায়ই ছিল চূরান্ত। বিচার বিভাগীয় সর্বোচ্চ মর্যাদা ও ছিল তাহাঁরই। মুহাজির ও আনসার জনগণ তো দ্বীন-ইসলাম কবুল করার সঙ্গে সঙ্গে রাসূলে করীম(স)-কে শুধু ধর্মীয় নেতাই নয়- সমাজ-রাষ্ট্রকর্তা হিসাবেও সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী রূপে স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। কজেই এই ধরনের চুক্তিতে তাহাদের কোনরূপ আপত্তি থাকার প্রশ্নই উঠিতে পারে না। কিন্তু ইয়াহুদী সমাজ তো সমগ্র আরবের উপরই নিজেদের সাংস্কৃতিক প্রাধান্যের দাবিদার ছিল। এতৎসত্ত্বেও তাহাদের পক্ষে এইরুপ ধারা সমন্বিত চুক্তিতে সম্মত হওয়া ছিল বিশ্বনবীর রাষ্ট্রনীতির একটা বিরাট মুজিজা।
মদীনা-চুক্তির উল্লেখযোগ্য ধারাসমূহ
মদীনা-চুক্তির ধারাসমূহ বিস্তারিতভাবে উদ্ধৃত করা এখানে সম্ভবপর নয়। সংক্ষেপে উহার গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি ধারা এবং তৎসংক্রান্ত সাধারণ পর্যালোচনা এখানে পেশ করা যাইতেছে।
ঘোষণাপত্রের প্রথম অংশ হইতে যে রাষ্ট্ররূপ দানা বাঁধিয়া উঠে,তাহা মুহাজির,আনসার ও সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ অন্যান্য গোত্র এবং লোকদের সমন্বয়ে গঠিত। এই সমস্ত লোক সুস্পষ্ট ভাষায় নবী করীম(স)-এর নেতৃত্বে মানিয়া চলার ও তাঁহার সহিত একত্রিত হইয়া শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য অঙ্গিকারবদ্ধ হইয়াছিল। নিজেদের মধ্যে শতধা-বিভক্তি ও বিভেদ থাকা সত্ত্বেও ইহারা সমগ্র বিশ্বসমাজ হইতে স্বতন্ত্র একটি একক(Unit)গড়িয়া তুলিয়াছিল।গোটা মুসলিম জনতা অধিকার ও কর্তব্যে সম্পূর্ণ অভিন্ন মর্যাদা গ্রহন করিয়াছিল। যুদ্ধ ও সন্ধি রাষ্ট্রীয় ও সামষ্ঠিক বিশয় রূপে গণ্য হইল। সামরিক দায়িত্ব সকলের জন্য অবশ্যই পালনীয় হইল। নিরাপত্তার অঙ্গীকার দেওয়ার অধিকার প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য নির্দিষ্ট হইল।চুক্তিবদ্ধ হওয়ার অধিকার প্রত্যেকের এবং একজনের চুক্তি সকলের জন্য বাধ্যতামূলক হইয়া গেল। ইহার ফলে রাষ্ট্রীয় সংস্থায় পূর্ণ ভ্রাতৃত্ব,সাম্য ও ব্যক্তি-স্বাধীনতার এক স্বর্ণযুগ সূচীত হইল।
এই চুক্তি অনুযায়ী মক্কার কুরাইশ পক্ষাবলম্বনে বা তাহাদের কোনরূপ সাহায্য ও আশ্রয়দানের অধিকার কাহার ও থাকিল না। উপরন্তু কুরাইশদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের অগ্রাভিযানে কোন রূপ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি কিংবা বিরুদ্ধতা করাও কাহারও পক্ষে সম্ভব থাকিল না।
সমস্ত ব্যাপারে সর্বোচ্চ ও সর্বশেষ আদালতের মর্যাদা পাইলেন স্বয়ং হযরত মুহাম্মাদ(স)।
অতঃপর আদালতী ব্যবস্থা আর এক ব্যক্তি বা একটি গোত্রের ব্যাপার হইয়া থাকিল না,বরং ইহা একটি সামষ্ঠিক ও সামাজিক মর্যাদা লাভ করিল।গোটা বিচার বিভাগীয় ক্ষমতাই কেন্দ্রীয় মর্যাদা পাইল।ইহাও ছিল একটি বিপ্লবাত্মক সিদ্ধান্ত।এই সিদ্ধান্তের ফলে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতা ও অবিমিশ্র সুবিচার সর্বত্র প্রাধান্য লাভ করিল।কোনরূপ পক্ষপাতিত্ব কিংবা স্বজন-প্রীতি বা আত্মীয়-প্রীতির সামান্য পথ ও উন্মুক্ত থাকিল না। সমস্ত মুসলমান সামগ্রিকভাবে এই জন্য দায়ী হইল যে, কেহ কাহারও উপর অত্যাচার করিতে পারিবেনা;কেহ কাহারও অধিকার হরণ করিতে পারিবেনা।
মদীনা-চুক্তির দ্বিতীয় অংশ সম্পূর্ণরূপে ইয়াহুদীদের সহিত সম্পর্কিত ছিল।সমস্ত ইয়াহুদী জনগোষ্ঠী একটি সমষ্ঠি হিসাবে ফেডারেল পদ্ধতির ‘মদীনা নগর- রাস্ত্রের’সহিত যুক্ত হইয়াছিল।প্রথম ধারাটিতে বলা হইয়াছিল যে,ইয়াহুদী ও মুসলমানরা যুক্তভাবে যদি কোন যুদ্ধ করে, তাহা হইলে প্রত্যেকেই নিজের নিজের ব্যয়ভার বহন করিবে। উভয়ই নিজেদের ধর্ম পালনে পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করবে। এভাবে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ব্যাপারে ইয়াহুদীরা মুসলমানদের সমান অধিকার লাভ করিল। দেশ রক্ষার দায়িত্বে ইহারা পরস্পরের সাহায্যকারী হইল। অর্থাৎ মুসলমান যাহাদের বিরুদ্ধে লড়াই করিবে,ইয়াহুদীরাও তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে বাধ্য হইবে। মুসলমানরা যাহাদের সহিত সন্ধি করিবে,ইয়াহুদীরাও তাহাদের সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হইবে। এই সময় দেশরক্ষার-অর্থাৎ মদীনা নগর-রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষার ব্যাপারে পরস্পরের কার্যকর সাহায্য করাও উভয়ের কর্তব্য হইবে। এই ধরনের চুক্তির ফলে প্রতিরক্ষা (Defense) ব্যাপারটিও কেন্দ্রীয় বিষয়ে গণ্য হইল।অতঃপর রাসূলে করীম(স)মুসলিম ও ইয়াহুদী সমন্বয়ে গঠিত সম্মিলিত সেনাবাহিনীর প্রধান (Head and supreme) হইলেন। ইহাই রাসূলে করীম(স)-এর আর একটি বিরাট রাজনৈতিক সাফল্য।
রাসূলে করীম(স)ইয়াহুদিদের একান্ত আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কিছুমাত্র হস্তক্ষেপ করিতেননা।ইহার ফলে তাহাদের মনে যে বিদ্বেষ ও আশঙ্কার কালোমেঘ পুঞ্জিভূত হইয়াছিল,তাহা অতি সহজেই বিলীন হইয়া গেল। তাহারা নিজেরাই সোৎসাহে নিজেদের যাবতীয় ব্যাপারে রাসূলে করীম(স)-কেই সর্বোচ্চ বিচারক হিসাবে মানিয়া ইয়াছিল।আত্মীয়তার ভিত্তিতে তাহাতে কোনরূপ প্রভাব বিস্তার করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হইয়া গেল। এইভাবে জাহিলিয়াত যুগের সমস্ত বাতিল নীতির নিদর্শনাদি নিঃশেষে মুছিয়া ফেলা হইল। অবস্থা এই দাঁড়াইল যে,ইয়াহুদীরা নবী করীম(স)-কে শুধু নিজেদের প্রশাসক মানিয়াই ক্ষান্ত হইল না, সমস্ত মদীনাকে তাহারা একটি ‘হারাম’(সুরক্ষিত ও সংরক্ষিত এলাকা)ও বানাইয়া লইল।ইহাও রাসূলে করীম(স)-এর রাষ্ট্রনৈতিক প্রজ্ঞা ও ধীশক্তির একটা বিরাট পরাকাষ্ঠা ছিল।( পরবর্তী সময়ে অবশ্য ইয়াহুদিরা প্রকাশ্যে রাষ্ট্রবিরোধী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হওয়ার দরুণ মদীনা হইতে শেষ পর্যন্ত নির্বাসিত হইতে বাধ্য হইয়াছিল।)
মদিনা নগর-রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা ও উহার সংরক্ষণ ব্যবস্থার জন্য আভ্যন্তরীণ দৃঢ়তা বিধানের সঙ্গে সঙ্গে নগরীর উপকণ্ঠে বসবাসকারী গোত্রসমূহের সহিত মিত্রতার সম্পর্ক গড়িয়া তোলাও অপরিহার্য ছিল। এই উদ্দেশ্যে নবী করীম(স) পশ্চিম অঞ্চল ও সীমান্তবর্তী জিলাসমূহ পরিভ্রমণ ও পরিদর্শন করিয়া সেখানকার গোত্রসমূহের সহিত বেশ কয়েকটি চুক্তি স্বাক্ষর করনে। ফলে এইসব গোত্র মুসলমানদের সহিত প্রতিরক্ষার ব্যাপারে মিত্র শক্তি হইয়া দাঁড়াইল।অতঃপর মদীনার চতুর্দিকের গোত্রগুলি মুসলমানদের সহিত শত্রুতা করার পরিবর্তে বিশেষ সাহায্যকারী হইয়া উঠিল।
চূড়ান্ত পদক্ষেপ
মদীনার আভ্যন্তরীণ ও পারিপার্শ্বিক দিক দিয়া পূর্ণ নিরাপত্তা ও নিশ্চিন্ততা লাভ করার পর নবী করীম(স) মক্কার কুরাইশদের সহিত দশ বছরের জন্য সন্ধি-চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এই চুক্তি “হুদাইবিয়া’ নামক স্থানে সম্পাদিত হওয়ায় ইতিহাসে ইহা ‘হুদাইবিয়া সন্ধি’ নামে পরিচিত।এই চুক্তি প্রকৃতপক্ষে মুসলমানদের জন্য ‘ফতহুম-মুবীন’-‘সুস্পষ্ট ও সমুদ্ভাসিত বিজয়’-নামে আল্লাহ্র কালাম কুরআন মজীদেই অভিহিত হইয়াছে। এই সন্ধি-চুক্তি সাক্ষরিত হওয়ার পর নবী করীম(স) সমগ্র আরব দেশে ব্যাপক ও সর্বাত্মকভাবে ইসলাম প্রচারের অবাধ ও নির্বিঘ্ন সুযোগ লাভ করিলেন। সেই সঙ্গে ইয়াহুদীদের শক্তি কেন্দ্র খায়বর হইতেও তাহাদিগকে চিরতরে ও সমূলে উচ্ছেদ করার উপায় হইয়া গেল।খায়বরের দুর্ভেদ্য দুর্গপ্রাকার জয় করার পর নবী করীম(স) সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ ও রক্তপাতহীন নিয়মে মক্কা শরীফ জয় করিতে সমর্থ হইলেন। অষ্টম হিজরী সনে মক্কা বিজয়ের পর নবী করীম(স) সমগ্র আরব উপদ্বীপটিকে ইসলামের একক ও নিরংকুশ শাসনাধীনে ঐক্যবদ্ধ করিয়া লইতে সমর্থ হইলেন। এইভাবে তিনি নিজের জীবনেই ইসলামী রাষ্ট্রকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর সংস্থাপিত করিয়া দিয়াছিলে।
বলা বাহুল্য,রাসূলে করীম(স) প্রতিষ্ঠিত এই রাষ্ট্রটি নিছক একটি রাষ্ট্রমাত্র ছিল না। ইহা ছিল বাস্তবে অস্তিত্বহীন একটি আদর্শবাদের পূর্নাঙ্গ বাস্তবায়ন।যে বীজটি আরব ভূ-খন্ডেরই একটি নির্জন স্থানে অতিশয় গোপনে উপ্ত হইয়াছিল একুশ বৎসর পূর্বে, উত্তরকালে তাহাই এক বিরাট মহীরুপে পরিণত হইয়া সমগ্র আরব দেশকে নিজের সুশীতল ছায়াতলে আনিয়া বিশ্বমানবতার জন্য চিরস্থায়ী এক আলোক কেন্দ্র(Light House)স্থাপন করিয়া দিয়াছিল। অনন্তকাল পর্যন্ত দুনিয়ার মানুষের জীবনে এই আলক-কেন্দ্র হইতে অজস্র ধারায় আলোকচ্ছটা বিচ্চুরিত হইতে থাকিবে এবং অত্যাচার-নিপীড়নে জর্জরিত দিশাহারা মানুষ উহা হইতেই মুক্তি ও কল্যাণ পথের নির্ভুল সন্ধান লাভ করিতে থাকিবে।
নবী-প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য
এইখানে নবী করীম(স) প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র ব্যবস্থার বিশেষত্ব ও বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা আবশ্যক। সংক্ষেপে তাহাই পেশ করা যাইতেছে।
(১)নবী-প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র সামাজিক-সামষ্ঠিক চুক্তি ও প্রতিশ্রুতির(Social Contract)ভিত্তিতে গড়িয়া উথা পৃথিবীর সর্বপ্রথম রাষ্ট্র ব্যবস্থা। মানব ইতিহাসে এই ধরনের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কোন দৃষ্টান্ত খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। নবুয়্যাতের ত্রয়োদশ বৎসর মদীনার লোকেরা স্বেচ্ছায় ও সাগ্রহে নবী করীম(স)-এর হাতে যে ‘বায়’আত’ করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে নিজেদের ধর্মীয় নেতার সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক নেতা ও শাসকও মানিয়া লইয়াছিলেন, উত্তরকালে তাহাই পূর্ণ পরিণতি লাভ করিয়াছিল একটি পূর্নাঙ্গ সর্বাত্মক রাষ্ট্র ব্যবস্থায়।
(২)এই রাষ্ট্র ব্যবস্থার সার্বভৌমত্বের(Sovereignty) উৎস ছিল মহান আল্লাহ্র সত্তা-সম্পূর্ণ নিরক্কুশভাবে।সার্বভৌমত্ব বলিতে যাহা বুঝায়,তাহাতে অন্য কাহারও-স্বয়ং নবী করীম(স)-এর কোন অংশ ছিল না। হযরত মুহাম্মাদ(স) আল্লাহ্র রাসূল হিসাবে কুরআনী বিধানের ভিত্তিতে আইন প্রবর্তন ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করিতেন।সার্বভৌমত্বের এই প্রশ্নটিই ইসলামী রাষ্ট্র ও দুনিয়ার অন্যান্য রাষ্ট্র দর্শনের মাঝে আকাশ-পাতাল পার্থক্যের ভিত্তিপ্রস্তর। রাসূলে করীম(স) আল্লাহ্র নিকট হইতে ‘অহী’পাইতেন। সেই অহীই ছিল আইনের মূল সূত্র।কিন্তু সার্বভৌমত্বের অধিকার হিসাবে তিনি নিজেকে কস্মিনকালেও পেশ করেন নাই।‘অহীর’ ব্যাখ্যা তিনিই প্রদান করিতেন। কিন্তু উহার বাস্তবায়নে নিজেকে কখনো বাদ(Exempted)দেন নাই। বরঞ্ছ অহীর মাধ্যমে তাঁহার নিজের কাজের ‘ত্রুটি’ও জনগনের সম্মুখে উদঘাটিত হইয়াছে। তিনি নিজেই নিজের ‘অপরাধ’ বিচারের জন্য লোকদের নিকট নিজেকে বারবার পেশ করিয়াছে। ইহার ফলে ‘বাদশাহ’কে বা ‘সর্বোচ্চ প্রশাসক’কে আল্লাহ্র আসনে বসাইবার সকল ধারণা ও নীতিমালা(‘বাদশাহ কখনও ভুল করিতে পারেন না’-বাদশাহকে কখনও অভিযুক্ত করা যাইতে পারে না ইত্যাদি)সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা প্রমাণিত হইয়া গেল। ইহাতে এই সত্যও প্রতিষ্ঠিত হইল যে,আল্লাহ্র নিরংকুশ সার্বভৌমত্বের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রে কোন ব্যক্তি ‘বাদশাহ’ বা স্বৈরতন্ত্রী হইতে পারে না। কোন দল বা গোষ্ঠীর পক্ষেও তাহা সম্ভব নয়। মানুষকে গোলাম বানাইবার অধিকার কাহারও থাকিতে পারে না।
(৩) ইহা একটি পুর্নাঙ্গ আদর্শভিত্তিক রাষ্ট্র(Ideological State)।নবী করীম(স)-ই ইতিহাসে সর্বপ্রথম লিখিত শাসনতন্ত্রের(Written Constitution) ভিত্তিতে রাষ্ট্র পরিচালনা শুরু করেন। ইহা বংশ, দেশমাতৃকা,বর্ণ,ভাষা ও নিছক অর্থনৈতিক একাত্নতা-ভিত্তিক রাষ্ট্র ছিল না। ইহা ছিল ইসলামী জীবনাদর্শের ধারক ও বাহক জাতিধর্ম নির্বিশেষে গোটা বিশ্ব মানবতাকে ইসলামের প্রতি আহ্বানকারী প্রথম রাষ্ট্র। ইসলামী আদর্শের পূর্ণ বাস্তবায়ন ও উহার সর্বাত্মক বিজয় অর্জন এবং ইহার মাধ্যমে জনগনের সার্বিক কল্যাণ বিধানই এই রাষ্ট্রের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল।
উল্লেখ্য যে, ইসলামী রাষ্ট্র পাশ্চাত্ত্যের ফ্যাসিবাদী বা তথাকথিত গণতন্ত্রবাদী রাষ্ট্রের মত স্বতঃই কোন লক্ষ্য নয়-অর্থাৎ রাষ্ট্রের জন্য রাষ্ট্র নয়;বরং একটি আদর্শ বাস্তবায়নের মাধ্যমে একটি উন্নততর ও মহত্তর লক্ষ্য অর্জনই ইহার উদ্দেশ্য। আর তাহা হইল আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের পরিপূর্ণ আনুগত্য এবং আল্লাহ্র পরম সন্তুষ্টি অর্জন।একটি ধর্মহীন(Secular) গণতান্ত্রিক বা জাতীয় রাষ্ট্র কোন উচ্চতর নৈতিক বিধানের অনুগত হয় না। কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্র হয় উহার সম্পূর্ণ বিপরীত। ইহাতে ধর্মীয় ও বৈজ্ঞানিক যাবতীয় ব্যাপার আল্লাহ্র বিধানের ভিত্তিতে সুসম্পুন্ন হইয়া থাকে।
(৪) ইসলামে ধর্ম ও রাষ্ট্র একই জিনিসের পার্থক্যহীন দুইটি দিক মাত্র। পার্থক্য শুধু শব্দের,মূল জিনিসের বা ভাবধারা দিক দিয়া ইহাতে কোন পার্থক্য নাই।এখানে যাহা ধরম,তাহাই রাজনীতি আর যাহা রাজনীতি,তাহাতেই ধর্ম নিহিত। ইসলাম স্বতঃই এক পুর্নাঙ্গ দ্বীন। মানব জীবন ও বিশ্ব-প্রকৃতির এমন কোন দিক নাই, যে বিষয়ে ইসলামের বিধান অনুপস্থিত। রাসূলে করীম(স) একই সঙ্গে আল্লাহ্র প্রতিনিধি হিসাবে জীবনের সর্বদিকে ও সর্বক্ষেত্রে অবিসংবাদিত নেতা। জীবনের বিভিন্নতা ও দ্বৈততা ইসলামের পরিপন্থী। বস্তুতঃরাষ্ট্রীয় ধর্মহীনতা বা ধর্মনিরপেক্ষতা উনবিংশ শতকের পোপতন্ত্রের প্রতিক্রিয়ার ফসল। বর্তমানে ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে ইহা সম্পূর্ণরূপে অতীত।ইহার ভিত্তিতে কোন রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বর্তমানে যুগে অসম্ভব। কেননা সংশয়বাদ,মানসিক অস্থিরতা ও স্বার্থবাদ(Utilitarianism) ছাড়া উহা বিশ্বমানবতার জন্য অন্য কোন অবদানই রাখিতে পারে নাই।
(৫) ইসলামী রাষ্ট্র প্রকৃত অর্থেই একটি গণ-অধিকারসম্পন্ন এবং জনমত ভিত্তিক কার্যকর রাষ্ট্র ব্যবস্থা।এখানে সমস্ত রাষ্ট্রীয় ব্যাপার জনগণের সমর্থন ও অনুমোদনের ভিতিতেই সুসম্পন্ন হইয়া থাকে বলিয়া রাষ্ট্রীয় মৌল নীতির বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলদের সাথে পরামর্শ ভিন্ন কার্যকর হইতে পারে না। এই নীতি রাসূলে করীম(স) কর্তৃক পুরাপুরি অনুসৃত।
ব্যক্তি স্বাধীনতা, সাম্য ও সুবিচার গণ- অধিকারসম্পন্ন রাষ্ট্র ব্যবস্থার ভিত্তি বিশেষ।এইগুলির যথাযথ বাস্তবায়ন ব্যতিত গণ-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবতা ধারণাতীত। রাসূলে করীম(স) প্রতিষ্ঠিত প্রথম ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থাই সর্বপ্রথম মানুষের প্রকৃত আজাদী কার্যকর হয়। ইসলামের কালেমা ‘লা-ইলাহা ইল্লালাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ’ ঘোষণায়ই ব্যক্তি-স্বাধীনতার বিপ্লবী ভাবধারা এক অপূর্ব চেতনায় বিধৃত। এক আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাহারোই –কোন-কিছুরই-একবিন্দু গোলামী করিতে প্রস্তুত না থাকার ইহা এক বিপ্লবাত্মক ঘোষণা ছাড়া আর কিছুই নয়।
আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমার মধ্যে মানুষ ইসলামী রাষ্ট্রে সম্পূর্ণ আজাদ ও স্বাধীন।এখানে প্রত্যেকরই অধিকার সুনির্দিষ্ট।কোন অবস্থায়ই কাহারও অধিকার হরণ করার কাহারও অধিকার নাই। ইসলামের সোনালি যুগে কোন ব্যক্তিকে কোন অবস্থায়ই তাঁহার মৌলিক অধিকার হইতে বঞ্ছিত করা হইত না। কাহারও ব্যক্তিগত মত প্রকাশ ও প্রচার, পেশা-গ্রহন,সভা-সম্মেলন অনুষ্ঠান বা যত্রতন্ত্র যাতায়াতে শরীয়াত-ভিত্তিক কোন কারণ ছাড়া কখনও কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা বা বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হইত না। কেননা এইরুপ করা ইসলামের দৃষ্টিতে সুস্পষ্ট জুলুম ছাড়া আর কিছুই নয়। এই কারণেই রাষ্ট্রপ্রধান রাসূলে করীম(স)-র সহিত মতবিরোধ করিয়া ভিন্নতর মত প্রকাশ করার অধিকারও প্রত্যেকেরই ব্যক্তিই পাইয়াছে।
এই রাষ্ট্রের সাম্য ও সততা দুইটি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। একটি আদম সন্তান হওয়া-ইহার কারণে সমস্ত মানুষই মূলগতভাবে সমান। আর দ্বিতীয় ভিত্তি ভ্রাতৃত্ব। সমস্ত মুসলমান পরস্পরের ভাই এবং সর্বতোভাবে অভিন্ন।
সুবিচার এই রাষ্ট্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। সমদৃষ্টি ও নিরপেক্ষতা এই রাষ্ট্রের স্থায়ী নীতি।নবী করীম(স) নিজে সবসময় সুবিচার নীতিকে ভিত্তি করিয়াই ফয়সালা করিতেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রে আইনের প্রয়োগ ছিল নির্বিশেষ।এমন কি,একটি বিচার কার্যের সময় ‘ফাতিমা চুরি করিলে উহার দণ্ডস্বরূপ তাঁহারও হাত কাটা যাইবে’ বলিয়া ঘোষণা করিয়া তিনি বিচার ও আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে সমস্ত দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির মূলোৎপাটন করিয়া দিয়াছেন।
(৬)ইসলামী রাষ্ট্র সঠিক অর্থে একটি জনসেবক ও জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র (Welfare State)ছিল। রাসূলে করীম(স) প্রতিষ্ঠিত এই রাষ্ট্রে জনগনের কেবল আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতাই করা হইত না,ইতিবাচকভাবে গন-অধিকার আদায় করা ও জনগনের দারিদ্র্য নির্মূল করার জন্যও চেষ্টা চালান হইত।পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের মত ‘অর্থোপার্জনের প্রতিযোগিতায় পরাজিত’দের সম্পূর্ণ অসহায় করিয়া রাখা এই রাষ্ট্রে মোটেই সম্ভবপর ছিল না। সকল লোকের সম্মুখে অর্থনৈতিক সুজগ-সুবিধার দ্বার সমানভাবে উন্মুক্ত করিয়া দেওয়ার পরও পিছনে পড়িয়া থাকা লোকদের আর্থিক নিরাপত্তার পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহন করা ছিল একমাত্র এই রাষ্ট্রেরই বিশেষত্ব। শুধু অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ব্যবস্থাই নয়, জনগনের নৈতিক মান উন্নতকরণ,তাহাদের মনে আল্লাহ্র ভয় জাগানো এবং দ্বীন ও শরীয়াত সম্পর্কে তাহাদিগকে সুশিক্ষিত করিয়া তোলার জন্যও নিরন্ততর গুরুত্ব সহকারে চেষ্টা চলানো হইত।
(৭)এই রাষ্ট্রের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হইল আল্লাহ্র নিকট জবাবদিহির তিব্রতম চেতনা।যাহা কিছুই করি না কেন,ব্যক্তিগত কাজ কিংবা জাতীয়-রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন-যে ধরনেই কাজ হউক না কেন-তাহা নিজের ঘরে গোপনে করা হউক,কি প্রকাশ্য-সব কিছুর মূলেই এই চেতনাটি প্রবল হইয়া থাকে। আর এই কারনেই এ রাষ্ট্রের কোন ক্ষেত্রেই আল্লাহ্র নাফরমানী,গণঅধিকার হরণ এবং জুলুম-নির্যাতনের কোন একটি ঘটনাও সংঘটিত হইতে পারিত না। এই দিকটির উপর আতদূর গুরুত্ব আরোপ করা হইত যে, রাষ্ট্রপ্রধান হইতে শুরু করিয়া নিম্নতম সহকারী কর্মচারী নিয়োগে সর্বাধিক আল্লাহভীরু ব্যক্তিকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হইত। ******(আরবী) ‘তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক আল্লাহ্ভীরু ব্যক্তিই তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্র নিকট সর্বাধিক সম্মানার্হ’ এই মূলনীতিই ছিল এই কাজের ভিত্তি।কেননা রাষ্ট্রনেতা বা সরকারী দায়িত্বশীল লোকেরা আল্লাহ্ভীরু না হইলে গোটা জাতিই চরম নাফরমান হইয়া যাইবে। তাহারা নীতিবান না হইলে গোটা জাতিই দুর্নীতিপরায়ণ হইয়া যাইবে-ইহা স্বাভাবিক। রাষ্ট্রনেতা ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ এবং সরকারী কর্মচারীগণ দুর্নীতিপরায়ণ না হইলে সাধারণ মানুষের পক্ষে দুর্নীতিগ্রস্ত হওয়া কক্ষনই সম্ভব হইতে পারে না। এমনকি তাহার ধারণাও করা যায় না। এই কথাটি যেমন সত্য, তেমনি ইহার বিপরীত কথাটিও সত্য। বিশ্বনবী প্রতিষ্ঠিত আদর্শ রাষ্ট্রের এই বৈশিষ্ট্যসমূহ ঐতিহাসিক। ইতিহাসে এইরূপ বৈশিষ্ঠ্যের অধিকারী অন্য কোন রাষ্ট্রেরি নাম খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।
বিশ্বনবী প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র-ব্যবস্থার এই বৈশিষ্ঠ্যসমূহ সম্মুখে রাখিয়া তুলনামূলক আলোচনা করিলে প্রমাণিত হইবে যে, দুনিয়ার অন্যান্য রাস্ত্রের-তাহা রাজনৈতিক হউক কি তথাকথিত ধর্মহীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র,পুজিবাদি রাষ্ট্র হউক কিংবা সমাজাতান্ত্রিক তথা কমিউনিস্ট রাষ্ট্র-কোন একটির সাথেও ইহার কোন তুলনা হয়না। একালের কোন ধরনের রাষ্ট্রই সার্বিক মানবিক কল্যাণের দিক দিয়া বিশ্ব নবী প্রতিষ্ঠিত এই রাষ্ট্রের সমতুল্য হইতে পারে না। দুনিয়ার এসব রাষ্ট্র ব্যবস্থা যেসব নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং মানব-কল্যাণের যেসব বড় বড় দাবি করা হয়, উহার অবৈজ্ঞানিকতা,যুক্তিহীনতা, অমানবিকতা ও অন্তঃসারশূন্যতা বহু পূর্বেই প্রমানিত হইয়াছে। সেসবের ব্যর্থতা সর্বজনস্বীকৃত। কিন্তু বিশ্বনবী প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্রের মূলনীতি যেমন স্বভাবসিদ্ধ,তেমনি শাশ্বত,চিরন্তন।ব্যক্তি মানুষ ও মানবসমষ্ঠির প্রকৃত কল্যাণ কেবল এই ধরনের রাষ্ট্র-ব্যবস্থার মাধ্যমেই অর্জন করা সম্ভব। অন্য কোন ধরনের রাষ্ট্র দ্বারাই ইহা সম্ভব হইতে পারে না।
জীবনের শেষদিন পর্যন্ত বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ(স) এই আদর্শ রাষ্ট্রের পরিচালনা করিয়া গিয়াছেন।‘খিলাফতে রাশেদা’ এই রাষ্ট্রেরই পরবর্তী নাম, ইহারই যথার্থ উত্তরাধিকারী।
খিলাফতে রাশেদা
বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর ইন্তেকালের পর যে চারজন প্রধান সাহাবী ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পালন করিয়াছেন, ইতিহাসে তাহাদিগকেই “খুলাফায়ে রাশেদুন”নামে অভিহিত করা হয় এবং তাঁহাদের পরিচালিত রাষ্ট্র-ব্যবস্থাকেই বলা হয় “খিলাফতে রাশেদা”। ‘খুলাফায়ে রাশেদুনে’র শাসন দীর্ঘকাল স্থায়ী না থাকিলেও বিশ্বের ইতিহাসে তাহা সর্বাধিক মর্যাদা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। শুধু মুসলিম ঐতিহাসিকগণই নহেন,অমুসলিম-এমন কিন মুসলিম-দুশমন ঐতিহাসিকগণও –খুলাফায়ে রাশেদুনের শাসন আমল্কে মানব-ইতিহাসের ‘স্বর্ণ-যুগ’ বলিয়া শ্রদ্ধা জানাইতে বাধ্য হইয়াছেন। বর্তমান পর্যায়ে আমরা ‘খিলাফতে রাশেদার’ বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য ও বৈশিষ্ঠ্য সম্পর্কে আলোচনা করিব।
খিলাফত
‘খিলাফত’ শব্দের আভিধানিক অর্থ ‘প্রতিনিধিত্ব’।ইহার ব্যবহারিক অর্থ, ‘অন্য কাহারো অপসৃত হওয়ার পর তাহার স্থানে উপবেশন করা’। এই শব্দটি স্বতঃই এই কথা প্রমাণ করা যে,উহাই আসল নয়, আসলের প্রতীক মাত্র;কায়া নয় ছায়া,দর্পণের প্রতিবিম্ব।অন্য কথায় মূল পদের স্থলাভিষিক্ত হওয়ারই নাম খিলাফত। ‘ইমাম’ শব্দও এই অর্থেই ব্যবহৃত হয় এবং ‘খলীফা’ ও ‘ইমাম’ এই শব্দদ্বয় একই ব্যক্তির দুইটি স্বতন্ত্র দিককে প্রকাশ করে। পূর্ববর্তী দায়িত্বশীলের প্রতিনিধি ও স্থলাভিষিক্ত হওয়ার দিক দিয়া সে খলীফা এবং সমসাময়িক যুগের জনগণের অনুসরণীয় ও সর্বাধিক গণ্যমান্য হওয়ার কারনে সে ‘ইমাম’ ও ‘নেতা’।বস্তুতঃ পয়গম্বরের স্থলাভিষিক্ত হওয়া এবং তাঁহার অন্তর্ধানের পর গোটা উম্মতের নেতৃত্ব দানকেই বলা হয় ‘খিলাফত’ ও ‘ইমামত’। নবী করীম(স) ইরশাদ করিয়াছেনঃ “তোমাদের পূর্বে বনী ইসরাইল গোত্রের নবী ও পয়গম্বরগণই নেতৃত্ব দান ও রাষ্ট্র পরিচালনা করিতেন;এক পয়গম্বরের অন্তর্ধানের পর আর এক পয়গম্বর আসিয়া তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইতেন। কিন্তু এখন(আমার পর) নবুয়্যাতির ক্রমিকধারা সম্পূর্ণ হইয়াছে(এখন আর কেহ নবী বা রাসূল হইবে না)।অতঃপর তোমাদের মধ্য হইতে খলিফাগণই অগ্রগামী হইবে”।
এই হাদিস হইতে এ কথা পরিস্ফুটিত হইয়া উঠে যে, পয়গম্বরীর প্রতিনিধিত্ব করাকেই খিলাফত বলা হয় এবং ইসলামে নবুয়্যাতের পর ইহাই সর্বাধিক মর্যাদাসম্পন্ন,শ্রদ্ধাভাজন ও পবিত্র দায়িত্বপূর্ণ পদ। এইজন্য ইসলামের ‘খলিফা’গন কুরআন ও সুন্নাতের মূলকে ভিত্তি করিয়া রাষ্ট্র পরিচালনা ও মানব-সমস্যার সমাধানের জন্য যেসব বিধান ও নির্দেশ দান করেন, তাহা অবশ্যই সর্বজনমান্য হইবে। রাসূলে করীম (স) পূর্বাহ্ণেই একথা ঘোষণা করিয়াছেনঃ ‘আমার পর আমার ‘হেদায়েতপ্রাপ্ত’ খলিফাগণকে মানিয়া চলিবে’। এই কারণেই খলীফা নির্বাচন করার সময় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির রাজনৈতিক বিচক্ষণতা ও শাসনতান্ত্রিক জজ্ঞতা-দক্ষতার দিকে যত-না দৃষ্টি দেওয়া উচিত,তদপেক্ষা অধিক লক্ষ্য আরোপ করিতে হইবে নবীর সংস্পর্শে(কিংবা নবীর অবর্তমানে তাঁহার আদর্শ অনুসরণে) তিনি নিজেকে কতখানি পরিশুদ্ধ করিতে সক্ষম হইয়াছেন এবং তাঁহার আধ্যাত্মিক জ্ঞান-বিদ্যা ও নৈতিক বৈশিষ্ট্য কতটুকু আছে,সেই দিকে। হযরত আবূ বকর সিদ্দিক,হযরত উমর ফারুক,হযরত উসমান গনী ও হযরত আলী মুরতাজা(রা)-এই চারজনকে পর্যায়ক্রমে খলীফার পদে নির্বাচন করায় উপরোক্ত নীতির নিগূঢ় তাৎপর্য ও যথার্থতা সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে।
বস্তুতঃইসলামে খিলাফতের দায়িত্ব কর্তব্য অত্যন্ত ব্যাপক ও সর্বাত্মক। যাবতীয় বৈষয়িক,ধর্মীয় ও তামাদ্দুনিক লক্ষ্য উহারই মাধ্যমে অর্জিত হইয়া থাকে।পয়গম্বরের আরব্ধ কার্যাবলীকে সচল ও প্রতিষ্ঠিত রাখা এবং সকল প্রকার সংমিশ্রণ হইতে উহার সংরক্ষণ ও উৎকর্ষ সাধন করা-এই সংক্ষিপ্ত বাক্য দ্বারাই খিলাফতের দায়িত্ব মোটামুটিভাবে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে।আর একটিমাত্র যুক্ত শব্দ দ্বারা ইহা বুঝাইতে হইলে বলা যায়-‘ইক্কামতে দ্বীন’।এই শব্দটিও এত ব্যাপক অর্থবোধক যে,দ্বীন ও দুনিয়ার সব রকমের কাজই উহার মধ্যে শামিল হইয়া যায়। নামায-রোযা,হজ্জ-যাকাত,আইন-কানুন,শাসন-শৃঙ্খলা ও বিচারব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা ও প্রচলন-এক কথায় সমস্ত তামাদ্দুনিক ও আধ্যাত্মিক কাজ সম্পাদনই খিলাফতের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। নবী করীম(স)-এর পবিত্র জীবন এই সব মহান দায়িত্ব সম্পাদনেই অতিবাহিত হইয়াছে। তাঁহার পর যাঁহারা তাঁহার প্রতিনিধি ও স্থলাভিষিক্ত হইয়াছেন,তাঁহারা নিজেদের সমগ্র জীবন এই উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করার জন্নই সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত করিয়াছেন।নবী করিম(স)-এর জীবনকাল হইতেই এইসব কাজে বিভিন্ন লোক জিম্মাদার হিসাবে নিযুক্ত ছিল। নামাযের ইমামতি করার জন্য,সাদকা ও যাকাত আদায় করার জন্য আলাদাভাবে লোক নিয়োগ করা হইয়াছিল। অন্যায় কাজের প্রতিরোধ ও ন্যায় কাজের প্রচার প্রসার এবং জনগণের পারস্পরিক বিবাদ-বিসম্বাদের নিরপেক্ষ বিচার ও ফয়সালার কাজ যোগ্যতাসম্পন্ন লোক দ্বারা সমাধা করা হইত।শত্রুর সহিত মোকাবিলা ও হইত। শত্রুর সহিত মোকাবিলা ও সৈন্য পরিচালনা এবং কুরআন শরীফ শিক্ষাদানের দায়িত্ব স্বতন্ত্র লোকের উপর অর্পিত ছিল। কিন্তু যেহেতু এই যেহেতু এই সমস্ত কাজই খিলাফতের মূল দায়িত্বের মধ্যে শামিল, সেইজন্য স্বতন্ত্রভাবে এইসব দায়িত্ব পালনের উপযোগী যোগ্যতা ও বৈশিষ্ট্য সবই এককভাবে এক খলীফার মধ্যে বর্তমান থাকা একান্তই আবশ্যকীয় ছিল। শুধু তাহাই নয়,আধ্যাত্মিক গুন-বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়া খলীফার মধ্যে নবীসুলভ শিক্ষা ও প্রজ্ঞা বলিষ্ঠভাবে বর্তমান থাকা জরুরী এবং নবী যাহাদের মধ্যে এই ধরনের আধ্যাত্মিক দক্ষতা দেখিতে পান, তাহাদিগকেই নিজের স্থলাভিষিক্ত করার কথা জীবিতাবয়স্থায়ই ইশারা-ইঙ্গিতে প্রকাশ করিয়া যান।অবশ্য অনাকাঙ্ক্ষিত বিশৃঙ্খলা,রক্তপাত ও অবস্থার পরিবর্তন খিলাফতের মূল লক্ষ্যকে চল্লিশ বৎসর পরই ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে এবং উহার কর্তৃত্বভার এমন সব লোকের হস্তে অর্পিত হইয়াছে,যাহারা কোন দিক দিয়াই এই গুরুত্বপূর্ণ পদের যোগ্য ছিল না, একথা অবশ্যই স্বীকার্য। কিন্তু বিশ্বনবীর হেদায়েত অনুযায়ী পরবর্তী খলীফা ও শাসকদের নির্বাচন করা হইলে মানব সমাজের চেহারা সর্বতোভাবে ভিন্ন রকমের হইত,তাহাতে সন্দেহ নাই।
কুরআন ও হাদীস হইতে খলীফার যোগ্যতা-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে যাহা কিছু জানা যায়, উহার দৃষ্টিতে যাচাই করিলে একথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, ‘খুলাফায়ে রাশেদুন’ই ছিলেন মুসলিম জাহানের খলীফা হওয়ার সর্বাধিক উপযোগী। কুরআন হাদীসের বর্ণিত গুন-বৈশিষ্ট্য তাঁহাদের মধ্যে পূর্ণমাত্রায় মওজুদ ছিল এবং সেই কারনে তাঁহারা খিলাফতকে সুষ্ঠু নীতিতে পরিচালিত করিতে পারিবে বলিয়া জনমনে পূর্ণ আস্থা বিদ্যমান ছিল।খিলাফতে রাশেদার দায়িত্ব পালনের জন্য কুরআনের দৃষ্টিতে নিম্নলিখিত গুন-বৈশিষ্ট্য অপরিহার্য মনে করা হইয়াছে। অতএব,নবী করীম(স)-এর পরে যাহাদের মধ্যেই এই গুণাবলী পরিস্ফুট হইবে,তাহারাই সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইবে।
(১)খলীফাকে প্রথম পর্যায়ের ‘মুহাজির’ হইতে হইবে এবং হোদাইবিয়ার সন্ধি,বদর ও তবুক যুদ্ধে শরীক ও সূরায়ে নূর অবতীর্ণ হওয়ার সময় উপস্থিত ছিলেন-এমন হইতে হইবে;
(২)বেহেশতবাসি হইবার সুসংবাদপ্রাপ্তদের মধ্যে গণ্য হইতে হইবে;
(৩)সিদ্দীক,শহীদ প্রভৃতি ইসলামী সমাজের উচ্চ পর্যায়ের লোকদের মধ্যে গণ্য হইতে হইবে।
(৪)নবী করীম(স)-এর কোন ব্যাবহার, কাজ বা কথা দ্বারা একথা প্রমাণিত হইতে হইবে যে,তিনি নিজে কাহাকেও খলীফা নিযুক্ত করিলে তাহাকেই নিযুক্ত করিতেন।
(৫)আল্লাহ্ তা’আলা রাসূলের নিকট যেসব ওয়াদা করিয়াছেন, তাহা তাঁহার সত্তা দ্বারা বাস্তবায়িত হওয়া সম্ভব হইতে হইবে।
(৬)তাঁহার কথা ইসলামী শরীয়াতে প্রমাণিত হইতে হইবে।
এই গুণাবলির বিচ্ছিন্নভাবে অসংখ্য সাহাবীর মধ্যে বর্তমান ছিল; কিন্তু এইগুলির পূর্ণ সমন্বয় ঘটিয়াছিল মাত্র চারজন সাহাবীর মধ্যে।ইঁহারা প্রথম পর্যায়ের মুহাজির ছিলেন,হোদাইবিয়া চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার সময় ইঁহারা উপস্থিত ছিলেন;বদর,ওহোদ,তবুক ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ জিহাদ-সংগ্রামে ইঁহারা ছিলেন অগ্রবর্তী।এইভাবে খিলাফতের যোগ্যতার জন্য অপরিহার্য গুণাবলির মধ্যে কোন একটি হইতেও ইঁহারা বঞ্চিত ছিলেন না। উপরন্তু ইঁহাদের প্রত্যেকেই সম্পর্কেই রাসূলে করীম(স)-এর সুস্পষ্ট মর্যাদাপূর্ণ ভবিষ্যদ্বাণী নির্ভরযোগ্য সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে।হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) সম্পর্কে নবী করীম (স)বলিয়াছেনঃ ‘আমার উম্মাতের মধ্যে তুমিই সর্বপ্রথম বেহেশতে প্রবেশ করিবে। ‘হাওযে-কাওসারে’ তুমিই হইবে আমার সঙ্গী;কেননা পর্বত গহ্বরে তুমিই আমার সাথী ছিলে’। হযরত উমর(রা) সম্পর্কে নবী করীম(স)-এর এই উক্তি বর্ণিত হইয়াছেঃ ‘উমরের কামনায়ই অসংখ্য আয়াত নাজিল হইয়াছে’।হযরত উস্মান(রা) সম্পর্কে রাসূল (স) বলিয়াছেনঃ ‘ফিরেশতাও যাহাকে সম্মান-শ্রদ্ধা জানায়,আমি কি তাঁহাকে সম্মান না জানাইয়া পারি?’ আরও বলিয়াছেনঃ ‘প্রত্যেক নবীরই বন্ধু থাকে,বেহেশতে উসমান হইবে আমার বন্ধু’।হযরত আলী(রা) সম্পর্কে নবী করীম(স)ইরশাদ করিয়াছেনঃ ‘তোমার সঙ্গে আমার হারুন ও মূসার ন্যায় সম্পর্ক স্থাপিত হউক, ইহা কি তুমি চাও না?আল্লাহ্ ও রাসূল যাহার প্রিয়পাত্র, আমি আগামীকাল তাঁহার হস্তেই ঝাণ্ডা তুলিয়া দিব’। এতব্দ্যতীত নবী করীম (স) ইহাদের গুণ-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আরো অনেক মূল্যবান কথাই বলিয়াছেন।সেইসব কথা দ্বারা একথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে,হযরতের দৃষ্টিতে তাঁহার অন্তর্ধানের পর ইঁহারাই ছিলেন খিলাফতের পদে নির্বাচিত হইবার সর্বাধিক উপযুক্ত এবং অধিকারী।
খিলাফতের মৌল আদর্শ
খিলাফত সম্পর্কিত আলোচনাকে গভীর ও ব্যাপকভাবে অনুধাবন করার জন্য উহার রাষ্ট্র-রূপকে যাচাই করা অত্যন্ত জরুরী। এই ব্যাপারে সর্বপ্রথম নেক চরিত্রবিশিষ্ট লোকদের প্রতিই এই ওয়াদা ঘোষিত হইয়াছে। তাই রাষ্ট্রের প্রতিটি(মুসলিম) নাগরিকই খলীফা মর্যাদাসম্পন্ন এবং খিলাফতের দায়িত্ব পালনের সমান সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার অধিকারী। এক্ষেত্রে কেবলমাত্র ব্যাক্তিগত চরিত্র,মানবীয় গুন-বৈশিষ্ট্য ও তাকওয়ার-পরহেজগারীর ভিত্তিতেই মানুষের মধ্যে পার্থক্য করা যাইবে।
তৃতীয়তঃ মানবতার ইতিহাসে যখনি আল্লাহ্র সার্বভৌমত্বের ভিত্তিতে কোন খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে সেখানেই সমাজের মধ্য হইতে কেবলমাত্র সর্বাধিক নেক ও পরহেজগার এবং উন্নত-আদর্শ চরিত্রবান লোকেরাই খলীফা হওয়ার-রাষ্ট্র পরিচালনা করার সুযোগ লাভ করিয়াছে। আর সাধারণ জনতা আল্লাহ্র দেওয়া মৌলিক অধিকার পূর্ণ ইনসাফ ও নিরপেক্ষভাবে ভোগ করিতে পারিয়াছে। কাহারও ক্ষেত্রে সেই অধিকারের এক বিন্দু হরণ করা কিংবা সংকুচিত করা হয় নাই,কাহারো স্বাভাবিক কর্মপথে বিন্দুমাত্র প্রতিবন্ধকতারও সৃষ্টি করা হয় নাই;বরং প্রত্যেকের স্বাভাবিক ক্ষমতা ও প্রতিভাকে আল্লাহ্র আইনসম্মত পন্থায় উৎকর্ষ ও ক্রমবিকাশ লাভের সুযোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।
ইসলামের বিধান অনুযায়ী প্রত্যেক বাক্তিই আল্লাহ্র নিকট জওয়াবদিহি করিতে বাধ্য। এই ব্যাপারে কাহাকেও অতি-মানবের আসনে বসাইয়া আল্লাহ্র সহিত শরীক করা যাইতে পারে না। ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান,খলীফা বা ‘আমিরুল মু’মিনীন’ পদে নির্বাচিত হওয়ার ব্যাপারে প্রত্যেক মুসলিম নাগরিকেরই সমান অধিকার রহিয়াছে। এক্ষেত্রে পদপ্রার্থী হওয়ার কিংবা পদলাভের জন্য চেষ্টা করার অধিকার যেমন কাহারো নাই, তেমনি নাগরিকদের অবাধ সম্মতিতে নির্বাচিত হইলে দায়িত্ব পালনেও সকলেই বাধ্য। খলীফা নির্বাচিত হওয়ার পর তাঁহার মর্যাদায় শুধু এতটুকু পার্থক্য ঘটে যে,জনগন নিজ নিজ খিলাফতের মর্যাদা ও অধিকার তাঁহার হস্তে অর্পণ করিয়াছে মাত্র।কেবল সে-ই খলীফা, অন্য কেহ খলীফা নয়, ইসলামী আদর্শবাদের দৃষ্টিতে একথা কিছুমাত্র সত্য নয়। খিলাফতের শক্তি নাগরিকদের সামাজিক ও সামগ্রিক নিয়ম-শৃঙ্খলা সংরক্ষণ ও অপরিহার্য আইন-কানুন জারিকরণের দায়িত্ব পালনে সর্বতোভাবে নিয়োজিত থাকে। এই শক্তির সংহতি বিধান ও ইহাকে সুনিয়ন্ত্রনে রাখার জন্য ইহা সাধারনের নির্বাচিত ও সর্বাধিক যোগ্যতম ব্যক্তির সত্তায় কেন্দ্রিভূত হওয়া আবশ্যক।
খলীফা বা ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচনের সময় ব্যক্তির জ্ঞান-বুদ্ধি, শিক্ষা-দীক্ষা,মন-মানস,বিচক্ষণতা ও সাংগঠনিক-যোগ্যতাই শুধু দেখিলে চলিবে না, তাহার চরিত্র কত পবিত্র,নির্ভরযোগ্য ও আস্থাভাজন,বিশেষ গুরুত্ব সহকারে তাহাও লক্ষ্য করিতে হইবে।
ইসলামী জীবন-ব্যবস্থা খলীফাকে ‘মাসুম’ বা নিস্পাপ ঘোষণা করে নাই।খলীফাকে নিস্পাপ ও নির্ভুল মনে করিয়া লওয়ারও কোন যুক্তি নাই। প্রতিটি মুসলিমই তাহার কেবল সরকারী দায়িত্ব পালন ও কার্য সম্পাদন সম্পর্কেই নহে,তাহার পারিবারিক ও ব্যক্তিগত জীবন-ধারারও সমালোচনা করিতে পারে।আইনের দৃষ্টিতে তাহার মর্যাদাও হইবে সাধারণ নাগরিকের সমান।আদালতে তাহার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা দায়ের করা যাইতে পারে এবং সে সাধারণ নাগরিকদের মতই বিচারকের সম্মুখে হাযির হইতে বাধ্য। সেখানে তাহাকে তথায় কোন প্রকার বিশিষ্টতা দান করা হইবে না।
খলীফার প্রতি আল্লাহ্র কোন অহি নাজিল হয় না; সুতরাং কুরআন ও সুন্নাহর ব্যাখ্যা-বাস্তবায়নের ব্যাপারে সে কোন বিশেষ মর্যাদা পাওয়ার দাবি করিতে পারে না।
খলীফা কেবল নিজস্ব মত অনুসারেই কার্য সম্পাদন করিতে পারে না,জনসমর্থিত ও যোগ্য-সুদক্ষ ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত মজলিসে শূরা’র(Parliament) সহিত পরামর্শ করিয়াই তাহাকে যাবতীয় কাজ সম্পাদন করিতে হইবে। মজলিসে শূরার সংখ্যাগরিষ্ঠ মত অনুসারেই সিদ্ধান্ত গ্রহন করিতে হয়,এ কথা ঠিক;কিন্তু তাহা সত্ত্বেও সংখ্যাধিক্য খিলাফতী শাসন-ব্যবস্থায় ভাল-মন্দবা করনীয়-বর্জনীয় নির্ধারণের কোন স্থায়ী মানদণ্ড নহে। তাই খলীফা কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে সংখ্যাগুরুর ফয়সালার সহিতও দ্বিমত পোষণ করিতে পারে এবং সে কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে যাহা সত্য বলিয়া প্রত্যয় করিবে,তদনুযায়ী কাজও করিতে পারে।অবশ্য এই সমগ্র ক্ষেত্রেই মুসলিম জনতা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করিবেঃখলীফা সামগ্রিকভাবে কুরআন-সুন্নাহ অনুসারে কাজ করে, না নিজস্ব খেয়ালখুশী অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা প্রয়োগ করে।দ্বিতীয় অবস্থার খলীফা ইসলামী জনতার নিকট হইতে একবিন্দু আনুগত্য পাইবার অধিকার রাখে না,বরং তাহার পদচ্যুতির ব্যবস্থা করাই তাহাদের কর্তব্য হইয়া পড়ে। এইদিক দিয়াও পাশ্চাত্য রাষ্ট্রদর্শন ও শাসনতন্ত্রের সহিত ইসলামী রাষ্ট্রদর্শন ও খিলাফতী গণ-অধিকারবাদের মধ্যে আসমান-জমিন পার্থক্য সুস্পষ্ট।
খুলাফায়ে রাশেদুন
ইতিহাসের যে পর্যায়টি হযরত আবূ বকর সিদ্দীকের(রা) খিলাফত হইতে শুরু করিয়া হযরত আলী(রা) পর্যন্ত বিস্তৃত, ইতিহাসে তাহাই হইতাছে ‘খিলাফতে রাশেদা’র যুগ। আর ৬৩২ ঈসায়ী(১১ হিজরী) হইতে ৬৬১ ঈসায়ী (৪০ হিজরী) পর্যন্ত মুসলিম জাহানের যাঁহার রাষ্ট্রনেতা ছিনেল,তাহাদিগকেই ‘খুলাফায়ে রাশেদুন’ বলিয়া অভিহিত করা হয়।ইঁহাদের মোট সংখ্যা চার এবং ইঁহাদের খিলাফত কালের মোট মুদ্দৎ ত্রিশ বৎসর মাত্র।(অবশ্য উমার ইবনে আব্দুল আজীজ (র)ও ইসলামী খিলাফতের নিয়ম অনুযায়ী নির্বাচিত ও দায়িত্ব পালনে সক্ষম হওয়ায় তিনিও ‘খুলাফায়ে রাশেদ’ রূপে গণ্য)
নবী করীম (স) যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন পর্যন্ত নবুয়্যাত,আইন প্রণয়ন,সর্ব ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দান,বিচার বিভাগ ও সৈন্য বাহিনী পরিচালনা এবং দেওয়ানী সরকারের যাবতীয় দায়িত্বপূর্ণ পদ হযরতের একক ব্যক্তিসত্তায় কেন্দ্রীভূত ছিল; তিনি একাই এই সমস্ত কাজের কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব করিতেন।তাঁহার ইন্তিকালের পর তাঁহার স্থলাভিষিক্ত কে হইবে, এই প্রশ্ন ইসলামী জনতার সম্মুখে অত্যন্ত প্রকট হইয়া দেখা দেয়।যেহেতু নবুয়্যাতের সমাপ্তি হইয়া গিয়াছে-অতঃপর কেহই নবী হইবেন না; কিন্তু রাসূলের স্থলাভিষিক্ত যে হইবে তাহাকে এই নবুয়্যাত ছাড়া ও নবুয়্যাত ব্যতিত আর সমস্ত দায়িত্বই পূর্বানুরুপ আঞ্জাম দিতে হইবে-এই কারনেও এই প্রশ্ন অত্যন্ত বেশি গুরুত্ব সহকারে নেতৃস্থানীয় ভাবিত ও বিব্রত করিয়া তোলে।নবী করীম(স)-এর নবুয়্যাত ও স্বভাব সুলভ নেতৃপদের উত্তরাধিকারী কেহই হইতে পারে না।অন্যদিকে তাঁহার কোন পুত্র-সন্তানও জীবিত ছিলনা।থাকিলেও তাহাতে খলীফা নির্বাচন সমস্যার কোন সমাধানই হইতে পারিত না। কাজেই এই দুইটি প্রশ্ন জটিলভাবে মাথা চাড়া দিয়া উঠিয়াছিলঃ
১-খলীফা কোন পরিবার বা গোত্র হইতে হইবে?
২-খলীফা নিয়োগের পন্থা কি হইবে?
কুরআন মজীদের কোথাও খিলাফতকে কোন বংশ বা গোত্রের জন্য বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয় নাই। হাদীসে যেখানে *****(আরবী)- ‘নেতা বা খলীফা কোরাইশদের মধ্য হইতে নিযুক্ত করিতে হইবে’ বলিয়া উল্লেখ পাওয়া যায়,সেখানেও স্পষ্ট ভাষায় নির্দেশ রহিয়াছেঃ
‘তোমাদের উপর কোন হাবশী গোলামও শাসক নিযুক্ত হইলে তোমারা তাহার অবশ্যই আনুগত্য করিবে’। কাজেই এতদুভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের পন্থা অনুসন্ধান করা আবশ্যক। একটু গভীর ও সুক্ষ দৃষ্টিতে চিন্তা করলেই বুঝিতে পারা যায় যে,মূলতঃএই দুইটি হাদিসই সত্য ও বাস্তব তত্ত্ব-ভিত্তিক ঘোষণা।ইসলামে খিলাফতকে কোন বংশ-গোত্র পরিবার কিংবা কোন ব্যক্তি বা শ্রেণীর জন্য বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয় নাই, এ-কথা চিরন্তন সত্য। ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় সকল সময় ও অবস্থায়ই এই মূলনীতি অনুযায়ী কাজ হইতে হইবে,ইহাতে সন্দেহ নাই;কিন্তু নবী করীম (স)যে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তাহাঁরই অব্যবহিত পড়ে উহার দায়িত্বভার পালনের জন্য কুরাইশ বংশের লোক অপেক্ষা অপর কোন বংশের লোক যে কিছুমাত্র যোগ্য বা দক্ষতাসম্পন্ন ছিল না, তাহাও এক অনস্বীকার্য ঐতিহাসিক সত্য।খিলাফতে রাশেদার ও ইহার পরবর্তী কালের ইতিহাসই এই কথার সত্যতা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে।কাজেই খিলাফতে রাশেদার চারজন খলীফাই কুরাইশ বংশের লোকদের মধ্য হইতে নির্বাচিত হওয়া সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত হইয়াছে। কেননা তাহা না হইলে তদানীন্তন আরব-সমাজের মধ্য হইতে বিশেষ যোগ্যতা ও দক্ষতা সহকারে খিলাফতের দায়িত্ব পালন করা অপর কাহারো পক্ষেই সম্ভব হইত না। কিন্তু ইহা কোন চিরন্তন ও শাশ্বত নিয়ম নহে; ‘খিলাফতে রাশেদা’র পরও খলীফার কুরাইশ বংশোদ্ভূত হওয়ার কোন শর্তই ইসলামী রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় স্বীকৃত নয়।১ {বলা বাহুল্য, ইসলামী রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরাও এই ধরনের কোন শর্তের কথা উল্লেখ করেন নাই।}
খলীফা নির্বাচনের বাস্তব ও সুস্পষ্ট কোন পদ্ধতি কুরআন-হাদীসে উল্লেখিত হয় নাই।মনে হয়,সেজন্য কোন বিশেষ পন্থাকে স্থায়ীভাবে স্বীকার করিয়া লওয়া এবং যুগ-কাল-স্থান-নির্বিশেষ সর্বত্র উহার অনুসরণকেই গোটা উম্মতের উপর বাধ্যতামূলকভাবে চাপাইয়া দেওয়া ইসলামের শাশ্বত বিধানের লক্ষ্য নয়। এই জন্য নির্বাচনের কোন বিশেষ পদ্ধতির(Form or Process) পরিবর্তে একটি শাশ্বত মূলনীতি পেশ করা হইয়াছে।বলা হইয়াছেঃ*****(আরবী) “ইসলামী আদর্শবাদীগণ নিজেদের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ পারস্পরিক পরামর্শের মাধ্যমে সম্পন্ন করিয়া থাকে’। আর রাষ্ট্রপ্রধান বা খলীফা নির্বাচনই যে মুসলিম সমাজে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় ও সামষ্ঠিক ব্যাপার এবং মুসলিম জনতার অবাধ রায় ও পরামর্শের ভিত্তিতেই যে ইহা সুসম্পন্ন হওয়া উচিত,তাহাতে কাহারো দ্বিমত থাকিতে পারে না। অতএব, জনমতের ভিত্তিতে খলীফা নির্বাচন করিতে হইবে- ইহাই হইল ইসলামী নির্বাচনের একমাত্র মূলনীতি। এই নীতিকে মুসলিম উম্মত বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কিভাবে প্রয়োগ করিয়াছে ও নির্বাচন-সমস্যার সমাধান করিয়া লইয়াছে,এখন তাহাই আমাদের বিচার্য।
খুলাফায়ে রাশেদুনের নির্বাচন
খলীফা নির্বাচনের উপরোল্লেখিত মূলনীতিকে খুলাফায়ে রাশেদুনের নির্বাচনের ব্যাপারে নিম্নলিখিত রূপে প্রয়োগ করা হইয়াছেঃ
(১)নবী করীম (স)-এর ইন্তেকালের পর মুসলিম উম্মতের দায়িত্বশীল নাগরিকগন ‘সকীফায়ে বনী সায়েদা’ নামক(টাউন হল কিংবা পরিষদ ভবনের সমমর্যাদাসম্পন্ন)স্থানে মিলিত হন এবং প্রকাশ্যভাবে দীর্ঘ ও বিস্তারিত আলোচনার পর সর্বসম্মতিক্রমে হযরত আবূ বকর(রা)-কে খলীফা নির্বাচিত করেন।উপস্থিত জনতা তখন-তখনি অকুণ্ঠিতভাবে তাঁহার আনুগত্যর শপথ(বায়’আত) গ্রহন করে এবং খলীফা নির্বাচিত হইয়াই তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব,কর্তব্য ও নীতি-নির্ধারকমূলক ভাষণ দান করেন।
(২)হযরত উমর ফারুক(রা)-এর নির্বাচনে স্বতন্ত্র পদ্ধতি অবলম্বিত হইয়াছে।প্রথম খলীফা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক(রা) তাঁহার গোটা ইসলামী জিন্দেগী ও খলীফা-জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী তথা বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে বুঝিতে পারিয়াছেন যে, তাঁহার পর খলীফা হওয়ার উপযুক্ত ব্যক্তি সমগ্র জাতির মধ্যে হযরত উমর(রা)অপেক্ষা দ্বিতীয় কেহ বর্তমান নাই।তাঁহার খিলাফতকালীন যাবতীয় ঘটনা ও গুরুত্বপূর্ণ সরকারী ও বেসরকারী কাজে হযরত উমর(রা)নিবিড়ভাবে শরীক ছিলেন;কুরআন মজীদ সঞ্চয়ন ও গ্রন্থাবদ্ধকরণও কেবলমাত্র তাহাঁরই ঐকান্তিক আগ্রহ,চেষ্টা ও পরামর্শে সম্পন্ন হইয়াছিল।হযরত আবূ বকর(রা)নিজের অভিজ্ঞতা ও প্রধান সাহাবাদের সহিত পরামর্শক্রমে হযরত উমর ফারুক(রা)-কেই পরবর্তী খলীফা নির্বাচনের জন্য মুসলিম জনতার নিকট সুপারিশ করিয়া গেলেন।মুসলিম জনসাধারন প্রথম খলীফার সুপারিশ ও নিজেদের নিরপেক্ষ ও অকুণ্ঠ রায়ের ভিত্তিতে হযরত উমর(রা) –কেই খলীফা হিসাবে নির্বাচিত করিল ও তাঁহার হস্তে বায়আত গ্রহন করিল।উমর (রা) খলীফা নির্বাচিত হইয়াই তাঁহার পূর্বসূরীর ন্যায় মুসলিম জনতাকে সম্বোধন করিয়া নীতি-নির্ধারণী ভাষণ দান করেন।
(৩)দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর(রা) যখন বুঝিতে পারিলেন যে,তাঁহার জীবন-পাত্র সম্পূর্ণ হইতে চলিয়াছে,তিনি আর বেশিক্ষন বাঁচিয়া থাকিতে পারিবেন না, তখন তিনি নিজের স্থলাভিষিক্ত ও পরবর্তী খলীফা নির্বাচনের প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন। সে জন্য তিনি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পদ্ধতি অবলম্বন করেন।তিনি ছয়জন শ্রেষ্ঠ ও নেতৃস্থানীয় সাহাবীর সমন্বয়ে একটি ‘নির্বাচনী বোর্ড’- আধুনিক পরিভাষায় ‘নির্বাচন কমিশন’-নিযুক্ত করিলেন।অন্যান্যদের ছাড়াও হযরত উসমান ও হযরত আলী(রা)ও এই বোর্ডের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।তাঁহার দৃষ্টিতে এই ছয় জনই খিলাফতের জন্য যোগ্য ব্যাক্তি ছিলেন। তিনি আদেশ করিলেন যে,তাঁহার অন্তর্ধানের পর তিন দিনের মধ্যেই যেন এই বোর্ড নিজেদের মধ্য হইতে সর্বাধিক যোগ্য ব্যক্তিকে খলীফা নির্বাচন করে।বোর্ড সুষ্টুরূপে তাহার দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করে এবং এই ব্যাপারে নিকটবর্তী ও দূরবর্তী মুসলিম নাগরিকদের রায় সংগ্রহ করে।মদীনার প্রতিটি ঘরে উপস্থিত হইয়া পুরুষদের সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রী লোকদেরও রায় জিজ্ঞাসা করা হয়।দূরাগত ব্যবসায়ী ও পর্যটকদের নিকটও রায় জিজ্ঞাসা করিতে ত্রুটি করা হয় নাই।এইভাবে ইসলামী নাগরিকদের সর্বাধিক রায় ও আলাপ-আলোচনার পর হযরত উসমান(রা)-কেই তৃতীয় খলীফা পদে নির্বাচিত করা হয়।
(৪)তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান(রা)-এর শাহাদাতের পর মদীনার পরিবেশ ফিতনা-ফাসাদের ঘনঘটায় অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। মিশর,কুফা ও বসরার বিদ্রোহীগণ মদীনায় প্রবল তাণ্ডবের সৃষ্টি করে।তখন প্রধান সাহাবীদের অধিকাংশই সামরিক ও সাংগঠনিক দায়িত্ব পালনের জন্য রাজধানীর বাহিরে অবস্থান করিতেছিলেন।এই অবস্থায় হযরত উসমান (রা)-এর শাহাদাতের পর ক্রমাগত তিন দিন পর্যন্ত খলীফার পদ শূন্য থাকে।শেষ পর্যন্ত দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পর হযরত আলী(রা)-কেই খলীফা নির্বাচিত করা হয়।
এই বিশ্লেষণ হইতে একথা প্রমাণিত হয় যে, খুলাফায়ে রাশেদুনের নিয়োগ ও নির্বাচনের ব্যাপারে একই ধরনের বাহ্যিক পদ্ধতি(Form Of Election)অনুসৃত না হইলেও প্রতিটি পদ্ধতিতেই জনমতকে নির্বাচনের ভিত্তিরূপে স্বীকার করা হইয়াছে এবং কোন ক্ষেত্রেই জনমতকে উপেক্ষা করা হয় নাই।বস্তুতঃপ্রকৃত খিলাফতের ইহাই মৌলিক ভাবধারা এবং জনগণের অধিকার সংরক্ষণ ও রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য প্রতিটি যুগে ও অবস্থায়ই ইহা কার্যকর হওয়া একান্ত অপরিহার্য। উপরন্তু মৌলিক ভাবধারাকে যথোপযুক্ত মর্যাদা ও গুরুত্ব সহকারে রক্ষা করিয়া রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচনের যে কোন বাহ্যিক পদ্ধতি গ্রহন করা যাইতে পারে।কেননা ইসলামে বাহ্যিক অবয়ব ও আকার-আকৃতির বিশেষ গুরুত্ব নাই;বরং জাতীয় ও তামদ্দুনিক ব্যাপারে উহার মৌলিক ভাবধারাই হইতেছে একমাত্র লক্ষ্য রাখার বস্তু।
খিলাফতে রাশেদার বৈশিষ্ট্য
ইতিহাস দর্শনের দৃষ্টিতে খিলাফতে রাশেদার ত্রিশ বৎসরকালীন শাসন ব্যবস্থার পর্যালোচনা করিলে উহার নিন্মলিখিত বৈশিষ্ট্যসমূহ গোটা মানব জাতিকে আকৃষ্ট ও বিমোহিত করেঃ
(১)খুলাফায়ে রাশেদুনের আমলে বিশ্বনবীর পবিত্র আদর্শ উজ্জল অনির্বাণ প্রদীপে পরিণত হইয়াছিল এবং সমগ্র পরিমণ্ডলকে উহ্য নির্মল আলোকচ্ছটায় উদ্ভাসিত করিয়া রাখিয়াছিল। খলীফাদের প্রতিটি কাজ ও চিন্তায় উহার গভীর প্রভাব বিদ্যমান ছিল।চারিজন খলীফাই বিশ্বনবীর প্রিয়পাত্র,বন্ধু ও বিশিষ্ট সহকর্মী ছিলেন।অপরাপর সাহাবীদের তুলনায় রাসূলের সাহচর্য ইঁহারাই সর্বাধিক লাভ করিয়াছিলেন।ইঁহারা ছিলেন হযরতের বিশ্বস্ত ও পরীক্ষিত এবং তাঁহার উদ্দেশ্যে উৎসর্গকৃত প্রাণ।একমাত্র হযরত আলী(রা) ব্যতিত আর তিনজন খলীফাই নবী করীম(স)-এর দ্বিতীয় কর্মকেন্দ্র ও শেষ শয্যাস্থল মদীনায় রাজধানী রাখিয়াই খিলাফতের প্রশাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করিয়াছিলেন।
(২)খিলাফতে রাশেদার অন্তর্ভুক্ত কোন খলীফার বংশ-গোত্র কিংবা পরিবার-ভিত্তিক অধিকার,উত্তরাধিকার বা প্রাধান্যের কোনই অবকাশ ছিল না। চারিজন খলীফা তিনটি স্বতন্ত্র পরিবার হইতে উদ্ভুত ছিলেন।বস্তুতঃইঁহারাই ছিলেন গোটা ইসলামী জনতার সর্বাপেক্ষা অধিক আস্থাভাজন।ক্রমিক পর্যায়ে ইঁহাদের নির্বাচনে প্রকৃত জনপ্রতিনিধিত্বের মৌলিক ভাবধারা কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই;বরং উহাই রক্ষিত হইয়াছে সর্বতোভাবে।তখন আধুনিক কালের পদ্ধতিতে নিরপেক্ষ সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইলেও কেবলমাত্র তাঁহারাই যে সর্বাধিক ভোটে নির্বাচিত হইতেন,তাহাতে কোনই সন্দেহ থাকিতে পারে না।
(৩)খিলাফতে রাশেদার আমলে আইন রচনার ভিত্তি ছিল কুরআন ও সুন্নাহ।যে বিষয়ে তাহাতে কোন সুস্পষ্ট নির্দেশ পাওয়া যাইত না,সে বিষয়ে ইজতিহাদ পদ্ধতিতে রাসূলের আমলের বাস্তব দৃষ্টান্ত ও অনুরূপ ঘটনাবলির সামঞ্জস্যের প্রতি লক্ষ্য রাহিয়া ইহার সমাধান বাহির করা হইত এবং এই ব্যাপারে কুরআন ও হাদীস পারদর্শী প্রতিটি নাগরিকেরই রায় প্রকাশের সমান অধিকার স্বীকৃত ছিল।কোন বিষয়ে সকলের মতৈক্যের সৃষ্টি হইলেই,সে সম্পর্কে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হইত।ফিকাহ-শাস্রের পরিভাষায় ইহাকেই বলা হয় ইজমা। ইসলামী শরিয়াতে ইহা সর্বজনমান্য মূলনীতি বিশেষ।আর কোন বিষয়ে মতবৈষম্যের সৃষ্টি হইলে খলীফা কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে নিজস্ব রায় অকুণ্ঠিতভাবে প্রকাশ করিতেন এবং তদানুযায়ী কার্য সম্পাদন করিতেন।
(৪)খুলাফায়ে রাশেদুন অধিকাংশ ব্যাপারেই দায়িত্বশীল সাহাবীদের সহিত পরামর্শ করিতেন।সাধারণ ব্যাপারে তাঁহারাই মনোনয়ন অনুযায়ী ‘মজলিসে শুরা’র সদস্য নিযুক্ত হইতেন।কিন্তু রায়দানের অধিকার কেবলমাত্র নিযুক্ত সদস্যদের জন্যই নির্দিষ্ট ছিল না।
(৫)খুলাফায়ে রাশেদুনের আমলে রাজকীয় জাঁক-জমক ও শান-শকাতের কোন স্থান ছিল না।সাধারণ নাগরিকদের ন্যায় অতি সাধারণ ছিল খলীফাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা।তাঁহারা প্রকাশ্য রাজপথে একাকী চলাফেরা করিতেন;কোন দেহরক্ষী তো দূরের কথা,নামে মাত্র পাহারাদারও ছিল না।প্রতিটি মানুষই অবাধে খলীফার নিকট উপস্থিত হতে পারিত।তাহাদের ঘরবাড়ি ও সাজ-সরঞ্জাম ছিল সাধারণ পর্যায়ের।
(৬)খুলাফায়ে রাশেদুন ’ বায়তুল মাল বা রাষ্ট্রের অর্থ ভাণ্ডারকে জাতীয় সম্পদ ও আমানতের ধন মনে করিতেন।রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে মঞ্জুরী ব্যতীত নিজের জন্য এক করা-ক্রান্তি পর্যন্তও কেহ খরচ করিতে পারিতেন না।এতব্দ্যতীত নিজেদের পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনের জন্যও তাঁহারা নিজেদের ক্ষমতা ও পদাধিকার বলে বায়তুল মাল হইতে কিছুই ব্যয় করিতেন না।
(৭)তাঁহারা নিজেদেরকে জনগণের খাদেম মনে করিতেন।কোন ক্ষেত্রেই তাঁহারা নিজদগকে সাধারণ লোকদের অপেক্ষা শ্রেষ্ট ধারণা করিতেন না। তাঁহারা কেবল রাষ্ট্রীয় পর্যায়েই জননেতা ছিলেন না, নামায ও হজ্ব প্রভৃতি ধর্মীয় ব্যাপারেও যথারীতি তাঁহারাই নেতৃত্ব দিতেন।
খিলাফতে রাশেদার আমলে ধর্মীয় কাজের নেতৃত্ব ও রাষ্ট্রীয় কাজের কর্তৃত্ব বিচ্ছিন্ন ও বিভক্ত ছিল না;বরং এই উভয় প্রকার নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বই একজন খলীফার ব্যক্তি সত্তায় কেন্দ্রীভূত ও সমন্বিত হইয়াছিল।বস্তুতঃধর্ম ও রাজনীতির পৃথকীকরণ এবং ধর্মীয় কাজ ও রাষ্ট্রীয় কাজে দ্বৈতবাদ যেমন আধুনিক পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য, অনুরুপভাবে এতদুভয়ের একত্রীকরণ ও সর্বতোভাবে একমুখীকরণই ছিল খিলাফতে রাশেদার বৈশিষ্ট্য।
খিলাফতে রাশেদার রাশেদার রাষ্ট্র-রূপ
হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) খলীফা নির্বাচিত হওয়ার পর এক ব্যক্তি তাঁহাকে ******- ‘হে আল্লাহ্র খলীফা’ বলিয়া সম্বোধন করিলে তিনি সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিলেনঃ ‘আমি আল্লাহ্র খলীফা নহি,আমি আল্লাহ্র রাসূলের খলীফা’।
ঐতিহাসিকগণ খলীফার এই উক্তিকে তাঁহার স্বভাবসুলভ অতুলনীয় বিনয় ও স্বীয় তুচ্ছতাবোধের অকাট্য প্রমাণ মনে করিয়া লইয়াছেন। কিন্তু রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে কথাটির বিশ্লেষণ করিলে ইহা হইতে ‘খিলাফতে’র গভীর তাৎপর্য সুস্পষ্ট হইয়া উঠে।বস্তুতঃপ্রাথমিক যুগে মুসলমানদের হৃদয়ে খিলাফতের যে রাষ্ট্ররূপ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল,হযরত আবূ বকরের এই উক্তি তাহারই সম্প্রকাশক।
বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর পূর্বে ও পরে কালের স্রোতে শত শত বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে।এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে শত-সহস্র রাজা-বাদশাহ ও দেশ শাসক আসিয়াছে ও দুনিয়ার রঙ্গমঞ্চ হইতে বিদায় নিয়াছে। তাহাদের সম্পর্কে সমসাময়িক লোকদের ও প্রজা-সাদারণের দাবি ছিল,তাহারা ভূ-পৃষ্টে আল্লাহ্র স্থলাভিষিক্ত। এই কারনে তাহারা যে সম্ভ্রম-মর্যাদা ও পবিত্রতার অধিকারী, পৃথিবীর বুকে তাহা অন্য কাহারোই থাকিতে পারে না।মিশরের ফিরাউনী রাজা-বাদশাহদের আত্মাভিমান ও দাম্ভিকতা ঐতিহাসিক ব্যাপার হইয়া রহিয়াছে।একজন ফিরাউন *****(আরবী) ‘আমি তোমাদের প্রধান ও শ্রেষ্ঠ প্রভু’ বলিয়া যে দাবি করিয়াছিল, কুরআন মজিদেও তাহার উল্লেখ রহিয়াছে।দূর অতীতকাল হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত রাষ্ট্রকর্তাদের অধিকাংশই এইরূপ মানসিকতার পরিচয় দিয়া আসিয়াছে। বর্তমান কালেও ইহার দৃষ্টান্ত কিছুমাত্র বিরল নহে।এই ব্যাপারে যাহা কিছু অপূর্ণতা ছিল,প্রত্যেক যুগের তোষামোদকারী ধর্মযাজক ও পুরোহিতরা তাহার সম্পূর্ণ করিয়া তুলিতে একবিন্দু ত্রুটি করে নাই।রাজা –বাদশাহ ও দেশ শাসককে তাহারা ‘পূজ্য’ ও ‘আরাধ্য’ করিয়া তুলিয়াছে যুগে যুগে, দেশে দেশে। মিসর,বেবিলন,পারস্য,ভারতবর্ষ ও অন্যান্য বহু দেশের অবস্থাই ছিল এইরূপ।এইসব দেশের অধিকাংশ রাজা-বাদশাহ ও সর্বোচ্চ ক্ষমতাশালী ব্যক্তি নিজেকে ধরনী তলে ‘খোদার প্রতিনিধি’ বা ‘খোদার ছায়া’ মনে করিত।তাহাদের অসহায় দরিদ্র প্রজাসাধারণও তাহাদিগকে অনুরূপ মর্যাদা দানে কিছুমাত্র ত্রুটি করিত না।
মধ্যযুগের ইউরোপেও পাদ্রীরা রাজা-বাদশাহদের ইঙ্গিতে ও নির্দেশেই তাহাদিগকে মহান,সম্মানার্হ ও পবিত্র বলিয়া উচ্চতম মর্যাদা দান করিতেও কিছুমাত্র সংকোচ বোধ করিত না। এই মর্যাদা তাহারা আল্লাহ্র নিকট হইতে পাইয়াছে বলিয়াই পাদ্রীরা প্রচারণা চালাইত।ইহার ফলে তাহাদের ক্ষমতা হইত অপ্রতিদ্বন্দ্বী-সকল প্রশ্ন,আপত্তি ও সমালোচনার অনেক ঊর্ধ্বে, জনগণের নাগালের বাহিরে; তাহারা ‘খোদার প্রত্যক্ষ প্রতিনিধি’ রূপে বিবেচিত হইত।তাহাদের মুখনিঃসৃত প্রতিটি কথাই ‘খোদার নিকট হইতে অবতীর্ণ প্রত্যাদেশ’ রূপে গণ্য হইত।তাহাদের আদেশ-নিষেধ সরাসরি আল্লাহ্র প্রত্যক্ষ আদেশ-নিষেধ সমতুল্য এবং অবশ্য-মান্য মনে করা হইত।এই কারনে উহা অমান্য করা,প্রত্যাখ্যান করা বা উহার প্রতি বিন্দুমাত্র অবজ্ঞা প্রদর্শন করাও মহাপাপের শামিল হইয়া যাইত এবং তাহা ছিল কার্যতঃঅসম্ভব। পঞ্চদশ শতাব্দী-এবং কোন কোন জাতিতে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত-এই অবস্থাই বিরাজিত ছিল।এই সময় পর্যন্তকার ইউরোপ যদিও জ্ঞান-বিজ্ঞান, সভ্যতা-সংস্কৃতি ও শিল্প-কুশলতায় অনেক উন্নতি লাভ করিয়াছিল; কিন্তু অন্ধ বিশ্বাসের যে ঠুঁলি তাহাদের চক্ষুর উপর বসাইয়া দেওয়া হইয়াছিল, তাহা তখনো অপসারিত হয় নাই। উত্তরকালে ব্যক্তিক ও মানসিক স্বাধীনতা এবং সাম্যবাদের অগ্রসেনারা এইসব মানব ধ্বংসকারী ও মানবিক মর্যাদা হরণকারী রসম-রেওয়াজের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদের আওয়াজ তুলিয়া আকাশ-পাতাল মথিত করেন এবং উহার বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহ করিতে বাধ্য হন।অবশ্য এই অভিযানে হাজার হাজার মানুষকে মহামূল্য জীবনও উৎসর্গ করিতে হইয়াছিল।
রাজা-বাদশাহদের এই পদ-পবিত্রতা ও মহাসম্মানের ভাবধারা বিশ-জাতিসমূহের মধ্যে শত শত বৎসর পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।আজিকার ইউরোপ এই ভাবধারা হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে খুব বেশি দিন হয় নাই। এই প্রেক্ষিতে প্রথম খলীফা হযরত আবূ বকর সিদ্দীকি (রা)- এর উপরোক্ত ক্ষুদ্র উক্তিতে নিহিত বিনয় ও আত্ম-স্বার্থহীনতা বিচার্য। একটি লোক তাঁহাকে ‘খলিফাতুল্লাহ্’- আল্লাহ্র খলীফা বা আল্লাহ্র প্রতিনিধি বলিয়া সম্বোধন করিলে তিনি তাহা মানিয়া লইতে স্পষ্ট ভাষায় অস্বীকার করেন এবং বলেনঃ ‘আমি আল্লাহ্র খলীফা নহি। আমাকে রাসূলের খলীফা বলিয়া অভিহিত করতে পার’।
‘রাসূলের খলীফা’ কথাটিও কোনরূপ ব্যক্তিগত দাপট-প্রতাপ,শান-শওকাত ও শ্রেষ্ঠত্ব-বড়ত্ব বা নিরংকুশ কর্তৃত্ব প্রকাশকারী নয়।উহার মূল তাৎপর্য হইল আল্লাহ্র বিধানের ভিত্তিতে তাঁহারাই নির্ধারিত সীমা-সরহদের মধ্যে থাকিয়া মুসলমানদের নেতৃত্ব দান ও রাষ্ট্র পরিচালনায় রাসূলে করীম(স)-এর স্থলাভিষিক্ত বা প্রতিনিধি হওয়া মাত্র।কিন্তু যেসব বিষয়-ব্যাপার কেবলমাত্র রাসূলের জন্য নির্দিষ্ট, সেসব ক্ষেত্রে তাঁহার ‘স্থলাভিষিক্ত’ হওয়ার কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না,উহার চিন্তা বা ধারণাও ইহাতে স্থান পায় নাই।প্রথম খলীফা নির্বাচিত হওয়ার পর প্রদত্ত প্রথম নীতি-নির্ধারণী ভাষণের একাংশ হইতেই তাঁহার এই কথার সত্যতা প্রতিভাত হইয়া উঠে।ভাষণের সেই অংশটি এইঃ
‘আমাকে খিলাফতের এই দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছে বটে;কিন্তু আমি নিজেকে এই গুরুদায়িত্ব পালনের কিছুমাত্র যোগ্য মনে করি না। আল্লাহ্র শপথ!আমার ঐকান্তিক বাসনা ছিল,তোমাদের মধ্য হইতে অপর ব্যক্তি এই দায়িত্ব গ্রহন করিবে।এখন তোমাদের কেহ যদি মনে করে যে,রাসূলে করীম(স) যে যে কাজ করিয়াছেন সেইসব কাজও আমি করিব,তাহা হইলে মনে রাখিও, এই ধারণা বা আশার কোন ভিত্তি নাই।রাসূলে করীম(স) আল্লাহ্র বান্দাহ ছিলেন,ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।কিন্তু সেই সঙ্গে আল্লাহ্ তা’আলা তাঁহাকে মহান নবুয়্যাত ও রিসালাতের নিয়ামত দানে ধন্য করিয়াছিলেন এবং সরবপ্রকার গুনাহ্-খাতা হইতে তাঁহাকে মুক্ত ও পবিত্র ঘোষণা করিয়াছিলেন’।
‘আমিও আল্লাহ্রই বান্দাহ। কিন্তু তোমাদের মধ্য হইতে কাহারও তুলনায় আমি উত্তম ব্যক্তি নহি।তোমরা আমার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিবে।যদি দেখিতে পাও,আমি আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রদর্শিত পথে চলিতেছি, তাহা হইলে তোমারও আমার অনুসরণ করিতে থাকিবে।কিন্তু তোমার যদি আমাকে ‘সিরাতুল-মুস্তকীম’ হইতে বিচ্যুত ও বিভ্রান্ত দেখিতে পাও তাহা হইলে আমার ভুল ধরাইয়া দিয়া আমাকে সঠিক, সত্য ও সোজা পথে পরিচালিত করিবে’।
বলা নিষ্প্রয়োজন,হযরত রাসূলে করীম (স)-এর ইন্তেকালের পর হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) মুসলিম জনতার নেতৃত্ব ও ইসলামী রাষ্ট্র-সংস্থা পরিচালনার দায়িত্ব নিজ হইতে গ্রহন করেন নাই।উদার-উন্মুক্ত পরিবেশে প্রকাশ্য নির্বাচন এবং গণ-সন্তোষ ও সমর্থন অর্জিত হওয়ার পরই তিনি এই কাজে ব্রতী হইয়াছিলেন। আল্লাহ্ তা’আলা যেভাবে নিজের পক্ষ হইতে নিজের বাছাই ও মনোনয়নের মাধ্যমে হযরত মুহাম্মাদ (স)-কে নবী ও রাসূল বানাইয়াছিলেন,তেমনিভাবে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক(রা) কিংবা পরবর্তী খলিফাত্রয় আল্লাহ্ কর্তৃক মনোনীত হন নাই। তাহারা আল্লাহ্ প্রেরিতও ছিলেন না। অন্যান্য মানুষের তুলনায় তাঁহাদের আদর্শিক শ্রেষ্ঠত্ব ও বিশিষ্টতা সর্বজনজ্ঞাত ও অবশ্য স্বীকৃতব্য; কিন্তু এই শ্রেষ্ঠত্ব ও বিশিষ্টতা আল্লাহ্ কর্তৃক ঘোষিত নয়।দ্বিতীয়তঃইহা তাঁহাদের তাকওয়া পরহেজগারী সদগুণাবলীর অনিবার্য পরিণতি মাত্র।খিলাফতের কারণেও এই বিশিষ্টতা অর্জিত হয় নাই,রাসূল যেমন বিশিষ্ট হইয়াছিলেন নবুয়্যাত ও রিসালাতের কারণে।বস্তুতঃখলীফা পদ নিছক বৈষয়িক, খোদায়ী (Divine) নয়।উহার সহিত অলৌকিক ও খোদায়ীর আদেশ ও নির্দেশ দানের অধিকারী ছিলেন,যাহা আল্লাহ্র নাজিল করা বিধান-ভিত্তিক এবং রাসূলের উপস্থাপিত শিক্ষা ও ব্যাখ্যার সহিত সঙ্গতিপূর্ণ।আল্লাহ্র বিধান-পরিপন্থী ও রাসূলের শিক্ষা ও ব্যাখ্যার সহিত অসঙ্গতিপূর্ণ কোন নির্দেশ দেওয়ার কোন অধিকার যেমন তাঁহাদের ছিল না,তেমনি মুসলমান জনগণও সেই ধরনের কোন নির্দেশ মানিয়া লইতে আদৌও বাধ্য নয়। প্রথম খলীফা নিজেই তাঁহার প্রথম ভাষণে এই কথাটি সুস্পষ্ট করিয়া দিয়া বলিয়াছেনঃ********(আরবী)
আমার আনুগত্য করিতে থাকিবে যতক্ষণ আমি আল্লাহ্ এবং তাঁহার রাসূলের আনুগত্য করিয়া চলিতে থাকিব।কিন্তু আমি নিজেই যদি(আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের)নাফরমানী করি,তাহা হইলে আমার আনুগত্য করা তোমাদের কর্তব্য নয়।
পরবর্তী খলীফাদের উপাধি
হযরত আবূ বকর (রা)-এর পর হযরত উমর ফারুক(রা) খলীফা নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু তিনি নিজে ‘খলীফায়ে রাসূল’-‘রাসূলের খলীফা’নামে অভিহিত হইতে সম্মত হইলেন না। এই বিষয়ে সমাজের লোকদের সহিত পরামর্শ করা হয়।শেষ পর্যন্ত তিনি ‘আমীরুল মু’মিনীন’- ‘মুসলিম জনগণের রাষ্ট্রনেতা ও পরিচালক’ সম্বোধনে সম্মত হইলেন।পরবর্তী খলীফাদ্বয়ও এই সম্বোধনেই ভূষিত হইয়াছেন। ‘খলীফা’ শব্দে অভিহিত হইতে তাঁহারা রাযী হন নাই এইজন্য যে,উহা মানিয়া লইলে ‘খলীফায়ে রাসূল’-‘রাসূলের খলীফা’ এইরূপ সম্বোধনে অভিহিত হইতে হইত। আর ইহার ফলে পরবর্তী খলীফার সম্বোধনে এই শব্দটির পুনরাবৃত্তি ঘটিত তিনবার কিংবা ততোধিকবার আর ইহা অত্যন্ত বিদঘুটে,অশ্রুতি মধুর,অমার্জিত এবং নিতান্তই অশোভন হইয়া পড়িত।
হযরত উমর(রা)-এর ‘খলীফায়ে রাসূল’উপাধিতে ভূষিত হওয়ার পরিবর্তে ‘আমিরুল মু’মিনীন’ নামে সম্বোধিত হইতে সম্মৎ হওয়ার মূলে আরো একটি কারন নিহিত ছিল।হযরত আবূ বকর সিদ্দিকী (রা) যখন বলিয়াছিলেন,আমি আল্লাহ্র খলীফা নহি,আল্লাহ্র রাসূলের খলীফা’, তখন শব্দটি উহার আভিধানিক অর্থে (স্থালাভিষিক্ত)ব্যবহৃত হইয়াছিল এবং লোকদিগকে পরিস্কার ভাষায় জানাইয়া দেওয়া হইয়াছিল যে, রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনে রাসূলে করীম(সা)-এর স্থলাভিষিক্ত হওয়াই তাঁহার একমাত্র মর্যাদা। আভিধানিক অর্থ ছাড়া অন্য কোন অর্থে তখন এই শব্দটি ব্যবহৃত হইয়া থাকিলে উহার পরিবর্তে হযরত উমর(রা)-এর ‘আমিরুল মু’মিনীন’ শব্দ ব্যবহারে সম্মত হওয়ার কোনই কারন ছিল না।
‘আমীরুল মু’মিনীন’ পরিভাষা গ্রহনের অন্তরালে আরও একটি কারণ বিদ্যমান ছিল। ইসলামী রাষ্ট্র-ব্যবস্থা তখন সমগ্র আরব উপদ্বীপ ও অন্যান্য বিপুল বিস্তীর্ণ অঞ্চলে এক ব্যাপক বিপ্লব সৃষ্টি করিয়াছিল। এই বিপ্লবের গতি যেমন ছিল তীব্র,তেমনি ব্যাপক ও সর্বাত্মক।সমগ্র পৃথিবীর মানুষ সে বিপ্লবের রূপ দর্শনে বিস্ময়-বিমুগ্ধ ও হতবাক হইয়াছিল। কিন্তু আল্লাহ্র কিতাব ও রাসূলের সুন্নাতে এই পর্যায়ে কেবলমাত্র কতকগুলি মূলনীতিই দেওয়া হইয়াছিল,বিস্তারিত ও খুঁটিনাটি বিধান তাহাতে ছিল না। অবশ্য কুরআনে শু’রা- পারস্পরিক পরামর্শ গ্রহণকে রাষ্ট্র-ব্যবস্থার মৌল ভিত্তি ও বাস্তব কর্মপন্থারূপে ঘোষিত হইয়াছে।আল্লাহ্ তা’আলা রাসূলে করীম(স) কে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া দিয়াছেনঃ*******(আরবী) ‘হে নবী, জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় যাবতীয় ব্যাপারে লোকদের সহিত পরামর্শ কর’। মুসলমানদের আচরণ পদ্ধতি ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ও একস্থানে বলা হইয়াছে,******(আরবী) তাহাদের যাবতীয় জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় কাজকর্ম পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে সুসম্পন্ন হইয়া থাকে’।
এই দৃষ্টিতে খিলাফতে রাশেদার প্রত্যেক খলীফাকে যাবতীয় জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ কার্যাদি কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে ও ভিত্তিতে পারস্পরিক পরামর্শক্রমে সম্পন্ন করিতে হইত।এই কারণে তাঁহাদের মর্যাদা এক-একজন সেনাধ্যক্ষ হইতে ভিন্নতর কিছু ছিল না। সেনাধ্যক্ষ যুদ্ধসংক্রান্ত যাবতীয় কাজের ব্যাপারে মৌল হেদায়েত ও নির্দেশ মূল ক্ষমতাধর ব্যক্তির নিকট হইতেই লাভ করিয়া থাকে।কিন্তু যুদ্ধকালীন সৈন্য পরিচালনা(Operation) ও যুদ্ধ ময়দানের ক্রিয়াকলাপ ইত্যাদি সবকিছুই সেনাধ্যক্ষকে নিজেকেই এবং নিজের একক দায়িত্বেই সম্পন্ন করিতে হয়। খিলাফতে রাশেদাকেও রাষ্ট্র ও দেশ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য সমসাময়িক পরিস্থিতি অনুযায়ী শরীয়াতের সীমার মধ্যে থাকিয়া ও রাসূলে করীম(সা)-এর আদর্শ সম্মুখে উদ্ভাসিত রাখিয়া আদর্শবাদী জননেতাদের পরামর্শক্রমে নিজেকেই আঞ্জাম দিতে হইত।প্রথম খলীফা কোন ব্যাপারে বিদ্যমান পরিস্থিতির আলোকে কোন বিশেষ কর্মনীতি গ্রহন করিয়া থাকিলে দ্বিতীয়,তৃতীয় বা চতুর্থ খলীফাকে ও হুবহু ঠিক সেই কর্মনীতিই গ্রহন করিতে হইবে-অবস্থা ও পরিবেশ পরিস্থিতি যতই পরিবর্তিত হউক না কেন-এমন কোন বাধ্যবাধকতা অবশ্যই ছিল না। এই কারণেই দ্বিতীয় খলীফা ‘খলীফায়ে রাসূল’ ইত্যাদি ধরনের উপাধি গ্রহনের পরিবর্তে সম্পূর্ণ নূতন এবং দায়িত্ব ও পদমর্যাদা সহিত পুরাপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ উপাধি ‘আমিরুল মু’মিনীন’ গ্রহন করাই সমীচীন মনে করিয়াছিলেন।
হযরত আবূ বকর (রা) তাঁহার খিলাফত আমলের অত্যল্প সময়ের মধ্য সমগ্র আরব দেশে যে বিপ্লবের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, উহার প্রতি পর্যবেক্ষকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপে একথা স্পষ্ট হইয়া উঠে যে, নম্রতা, কোমলতা ও ক্ষমতাশীলতা এবং কঠোরতা ও অনমনীয়তার ক্ষেত্র ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে এবং কঠোরতার স্থানে কঠোরতা ও অনমনীয়তার ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে এবং কঠোরতার স্থানে কঠোরতা ও নম্রতা-নমনীয়তার স্থানে নম্রতা-নমনীয়তা অবলম্বিত না হইলে রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় পর্যায়ের কোন কাজই সুষ্ঠু ও যথার্থরূপে সম্পন্ন হইতে পারে না। শুধু হযরত আবূ বকর(রা)ই নহেন, পরবর্তী তিনজন খলীফার সাফল্য ও অসাধারণ শক্তি-সামর্থের পশ্চাতেও এ নিগূঢ় তত্ত্বই নিহিত যে, তাঁহারা অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সঠিক ও নির্ভুল পদক্ষেপ গ্রহনে সম্পূর্ণ সক্ষম ছিলেন।
সমসাময়িক আরবের রাজনৈতিক ব্যবস্থা
রাসূলে করীম (স)-এর সময় আরবদেশ অসংখ্য প্রকারের ধর্মমতের লীলাক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল।উহার উত্তর-দক্ষিণ অংশ পরস্পর হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ছিল। একাংশের অধিবাসীদের কোন সম্পর্ক অপরাংশের জনগণের সহিত ছিল না। উভয় অংশের লোকদের সাধারণ অবস্থাও কিছুমাত্র অভিন্ন ছিল না। ইয়েমেন ইরানীদের কর্তৃত্বাধীন ছিল। খৃষ্টধর্ম ও মূর্তি পূজার ধর্ম সেখানে পাশাপাশি চলিতে ছিল। তাহাদের হেমায়ারী ভাষা কুরাইশদের ভাষা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্নতর ছিল। উপরন্তু ইয়েমেন ছিল কয়েক শতাব্দী কাল ধরিয়া সভ্যতা ও সংস্কৃতি পাদপীঠ। পক্ষান্তরে হিজাজের লোকেরা ছিল অসভ্যতা ও যাযাবরত্তের প্রতীক।এই অঞ্চলে মক্কা,ইয়াসরীব(মদীনা) ও তায়েফ-মাত্র এই তিনটি স্থান ছিল ‘শহর’ নামে অভিহিত হওয়ার যোগ্য। আর হিজাজের বিশাল অঞ্চলের মধ্যে অবস্থান ছাড়া এই তিনটি শহরের মধ্যে পারস্পরিক কোন সম্পর্ক বা সাদৃশ্য ছিল না। অবশ্য এই শহরত্রয়ের লোকদের মধ্য আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপিত ছিল। কিন্তু এই তিনটি শহরের প্রশাসন ব্যবস্থা ছিল সম্পূর্ণ গোত্রবাদ ভিত্তিক এবং পরস্পরক বিচ্ছিন্ন। মক্কায় মূর্তি পূজার প্রাবল্য ও ব্যাপকতার সঙ্গে সঙ্গে খৃস্টবাদেরও আনুকূল্য ছিল। মদীনায় ইয়াহুদী গোত্রসমূহ বাহ্যতঃ পরাক্রমশালী হইলেও মূর্তি পূজারীদের সংখ্যা ছিল গরিষ্ঠ। এই বিশাল আরব উপদ্বীপে যখন তাওহীদের বাণী ধ্বনিত হইল এবং আল্লাহ্ তা’আলা আরবের চতুর্দিকে দ্বীন-ইসলামকে প্রসারিত করিতে চাহিলেন, তখন তিনি উহার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাও সম্পূর্ণ করিয়া দিলেন। ইয়েমেন পারসিকদের দাসত্ব হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিল।তৎসঙ্গে সমস্ত বৈদেশিক প্রভাব-প্রতিপত্তি হইতেও তাহারা সম্পূর্ণ মুক্ত হইয়া গেল।মক্কা বিজয়ের পর সমগ্র আরবদেশে ইসলাম তীব্র গতিতে প্রচারিত হইতে লাগিল।হিজাজের পর অন্যান্য আরব অঞ্চলেও ইসলাম প্লাবনের মতই বিস্তার লাভ করিল।এইভাবে অতি অল্প সময়ের মধ্যে সমগ্র আরব উপদ্বীপ ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় লাভে ধন্য হইল। এই বিশাল অঞ্চলের সমস্ত জনতা একই আদর্শে দীক্ষিত হইয়া গেল।রাসূলে করীম(স)-এর প্রতি ঈমান এবং তাঁহার প্রচারিত দিন-ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসাবে গ্রহণের ব্যাপারে সমগ্র আরব অভিন্ন ও ঐক্যবদ্ধ হইয়া উঠিলেও প্রতিটি গোত্র নিজ নিজ স্থানে সম্পূর্ণ স্বাধীন ও সার্বভৌম মর্যাদায় অভিষিক্ত ছিল। অবশ্য ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ ‘রুকন’-যাকাত-মদীনার রাজধানীতে পাঠাইতে সব অঞ্চলের লোকেরাই সমানভাবে বাধ্য ছিল।
দ্বীন ও ধর্মের ঐক্য ও একত্ব আরবদের রাষ্ট্র ব্যবস্থায় বিপ্লব সৃষ্টির হিসেবে কাজ করিয়াছে।মদীনার চতুর্দিকে বসবাসকারী গোত্রসমূহ রাসূলে করিম(স)-এর সহিত মিত্রতার চুক্তি সম্পন্ন করিয়া লইয়াছিল।তিনি যখন মক্কা বিজয়ের অভিযানে যাত্রা করিলেন,তখন এইসব গোত্র চুক্তি অনুযায়ী কাফেলার সহিত শামিল হইয়াছিল।মক্কা বিজয়ের পর সেখানকার গোত্রসমূহ সাগ্রহে ইসলাম গ্রহন করিল।অতঃপর তাহারাও ইসলামের বিজয় অভিযানসমূহে যোগদানের ইচ্ছা প্রকাশ করিল।হুনাইন ও তায়েফ যুদ্ধে ইহারা যথারীতি অংশ গ্রহন করে। এইভাবে ইসলাম যখন চতুর্দিকে বিস্তার লাভ করিল, তখন নবী করীম(স) আরব গোত্রসমূহের লোকদিগকে কুরআন মজীদ ও দ্বীনী বিষয়াদি শিক্ষা দানের জন্য লোক নিযুক্ত করিয়া চতুর্দিকে পাঠাইয়া দিলেন।কুরআন শরীফ ও দ্বীন-ইসলাম শিক্ষাদানের সঙ্গে সঙ্গে যাকাত আদায়ের দায়িত্বও কর্মচারীদের উপর ন্যস্ত করা হইল।অত্যল্প সময়ে সৃষ্ট এই দ্বীনী বিপ্লবের প্রভাবে সমগ্র অঞ্চলে রাজনৈতিক বিপ্লব সৃষ্টিও অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল।দ্বীন ও ধর্মের দিক দিয়া সমগ্র আরব এক ও অভিন্ন হইয়া উঠার পর রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক দিক দিয়াও এক অভিন্ন সত্তা ও সংস্থায় পরিণত হওয়া ছিল অত্যন্ত স্বাভাবিক পরিণতি। কিন্তু আরব বেদুঈনরা এই ধরনের রাজনৈতিক বিপ্লবের সহিত কিছুমাত্র পরিচিত ছিলনা। রাসূলে করীম(স)-এর অন্তর্ধানের পর তাঁহার স্থলাভিষিক্তেরও অনুরুপভাবে আনুগত্য স্বীকার করিতে হইবে,ইহা ছিল তাহাদের চিন্তা-ভাবনার অতীত।তাহার মনে করিত,রাসূলে করীম (স) উপস্থাপিত শিক্ষা,দ্বীন ও আদর্শ তো তাহাদের মন-মগজ ও জীবনে দৃঢ়মূল হইয়া বসিয়া আছে। ইসলামের পূর্নাঙ্গ বিধান তো তাহারা পালন করিয়া চলিবেই। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও রাজনৈতিক দিক দিয়া তাহারা হইবে সম্পূর্ণ স্বাধীন।প্রতিটি গোত্রই পূর্বের ন্যায় বাহিরের রাষ্ট্র ও সরকারের সর্ব প্রকার প্রভাব হইতে থাকিবে সম্পূর্ণ মুক্ত ও বন্ধনহীন।
বস্তুতঃরাসূলে করীম (স)-এর অন্তর্ধানের পর আরব উপদ্বীপের দিকে দিকে যে বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলিত হয়, তাহার মূলে ছিল স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতার এই অনমনীয় ভাবাধারারই প্রাবল্য। অধিকাংশ আরব গোত্রেরই অবস্থা ছিল এইরূপ। কিন্তু প্রথম খলীফা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) চাহিয়াছিলেন, আরব গোত্রসমূহ রাসূলে করীম (স)-এর জীবদ্দশায় যেরূপ ইসলামী রাষ্ট্রের অধীন হইয়াছিল, সেই অবস্থার বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হইতে দেওয়া হইবে না। কিন্তু আরব গোত্রসমূহ তাহাদের হৃত রাজনৈতিক স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার হইবে বলিয়া মনে-প্রাণে আশা করিয়াছিল। হযরত আবূ বকর (রা) তাঁহার সাচ্চা ঈমানী শক্তির বলে বলিয়ান হইয়া আপন সংকল্পে অবিচল থাকিলেন।মুসলমান হিসাবে প্রত্যেক স্ব স্ব দায়িত্ব পালন করুক এবং ইসলামের উপস্থাপিত ঐক্য ও সংহতির আদর্শ সকলেই পুরোপুরি মানিয়া চলুক, ইহাই ছিল তাঁহার আন্তরিক বাসনা।তিনি স্পষ্টতঃজানাইয়া দিলেন যে, রাসূলের জীবনকালে যাকাত, ওশর ও খারাজ বাবদ যে সম্পদ মদীনায় প্রেরিত হইত, তাহা অবশ্যই আদায় করিতে হইবে। কিন্তু আরব গোত্রসমূহ সেজন্য প্রস্তুত হইতে পারিতে ছিল না। তাহারা স্পষ্ট ভাষায় বলিতে শুরু করিল, রাসূলে করীম (স)-এর ব্যাপারে ছিল সম্পূর্ণ ভিন্নতর।তিনি আল্লাহ্র রাসূল ছিলেন।তাঁহার প্রতি অহী নাযিল হইত। তাঁহার পুর্ণাঙ্গ আনুগত্য স্বীকার করা মুসলিম মাত্রেই কর্তব্য ছিল। কিন্তু এখন অবস্থার পরিবর্তন হইয়াছে। এখন তদনুসারে রাষ্ট্র ব্যবস্থায়ও পরিবর্তন আনিতে হইবে। কিন্তু এই চিন্তা ও মানসিকতা কোনক্রমেই ইসলামী রাষ্ট্র সংস্থা গড়িয়া উঠার অনুকূল ছিল না।হযরত আবূ বকর (রা)প্রবল শক্তিতে এই নৈরাজ্যমূলক মানসিকতা নির্মূল করিয়া দিলেন।এই পর্যায়ে তিনি যে গভীর বিচক্ষণতাপূর্ণ ও বুদ্ধিসম্মত পন্থা গ্রহন করিয়াছিলেন, তাঁহার ফলে সমগ্র আরবদেশ একটি অভিন্ন রাষ্ট্র-সংস্থার অধীনে সুসংগঠিত ও সুসংবদ্ধ হইয়া উঠিল।তিনি দেশ শাসন,রাষ্ট্র পরিচালনা ও যুদ্ধ-সন্ধির ব্যাপারে সমগ্র গোত্রসমূহকে ঐক্যবদ্ধ করিয়া লইলেন। সকল পর্যায়ের লোকদের সহিত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে পরামর্শ গ্রহণের নীতি কার্যকর করিলেন। ফলে সকল গোত্রই নিজদিগকে ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনায় সমান অংশীদার মনে করিতে শুরু করিল।প্রতিটি ব্যক্তি ও গোত্র সর্বক্ষেত্রে সমান গুরুত্ব, মর্যাদা ও অধিকার লাভ করিতে পারিয়া বিপুল উৎসাহ –উদ্দিপনা সহকারে রাষ্ট্র-সংস্থার আনুগত্যে নিজেদের সোপর্দ করিল।খলীফাই ছিলেন এই আনুগত্যের কেন্দ্রীয় ব্যক্তি সত্তা। তাঁহার যে কোন আদেশ ও নিষেধ পালনতাহাদের জন্য অবশ্য কর্তব্য,এই ব্যাপারে তাহাদের মধ্যে আর কোন মতদ্বৈততা থাকিল না।
খিলাফতের রাষ্ট্র-রূপ
ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার আদর্শিক পরিচিতি কি?উহা কোন্ ধরনের রাষ্ট্র ব্যবস্থা? উহা কি নিরেট থিওক্রাসী(Theocracy), যেখানে কোন আল্লাহ্প্রিয় ব্যক্তি স্বয়ং কিংবা যাজক সম্প্রদায় শাসন কার্য পরিচালনা করেন? কিংবা উহা আধুনিক পরিভাষা অনুযায়ী একটি গণতান্ত্রিক(Democrative) অথবা কোন স্বৈরতান্ত্রিক(Autocracy) শাসন? কিংবা উহা এক ধরনের রাজতন্ত্র? এই প্রশ্ন একালের বহু চিন্তাবিদকে পর্যন্ত বিভ্রান্ত করিয়াছে। কিন্তু ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞানও যাঁহাদের আছে, তাঁহারা এই ধরনের প্রশ্নে কিছুমাত্র বিচলিত হইতে পারেন না। কেননা খিলাফত যে কোনক্রমেই পোপতন্ত্র বা থিওক্রাসী ধরনের শাসন ব্যবস্থা নয়, তাহা বুঝিবার জন্য বিশেষ পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন হয় না। প্রাচীন কালের ফিরাউন কিংবা আধুনিক ইউরোপসহ দুনিয়ার অন্যান্য রাজা-বাদশাহরা যে ধরনের শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করিয়াছে ও করিতেছে, খিলাফতের শাসনব্যবস্থার সহিত উহার দূরতম সম্পর্ক বা সামান্যতম সাদৃশ্যও খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।আধুনিক ধরনের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও উহাকে বলা যাইতে পারে না- যদিও সর্বজনীন মূল্যবোধ এবং জনগণের অধিকার ও ব্যক্তি স্বাধীনতার সুযোগ-সুবিধা উহাতে ছিল পূর্ণমাত্রায় কার্যকর,যা পাশ্চাত্যের ধর্মহীন গনতন্ত্রে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।
কোন একজন খলিফাও নিজেকে আল্লাহ্ কর্তৃক মনোনীত, আল্লাহ্র সহিত বিশেষ সম্পর্কের অধিকারী কিংবা আল্লাহ্র নিকট হইতে প্রত্যক্ষ বিধান-ওহী- লাভ করার কোন দাবি কখনও করেন নাই। এইরূপ দাবি উত্থাপনকে তাঁহারা সম্পূর্ণ হারাম মনে করিতেন। কেননা প্রকৃতপক্ষেও ইহা ছিল সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। রাসূলে করীম (স)- এর ইন্তেকালের সঙ্গে সঙ্গে ওহী নাজিলের ধারা চিরতরে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। অতঃপর দুনিয়ার মানুষের নিকট জীবন, সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য মাত্র দুইটি ভিত্তিই অবশিষ্ট রহিয়াছে। একটি আল্লাহ্র কিতাব আর দ্বিতীয়ত রাসূলের সুন্নাত। আল্লাহ্ তা’আলা বিশ্ব মানবের জন্য সার্বিক ও পূর্ণাঙ্গ বিধান হিসেবে সর্বশেষ নবীর মাধ্যমে কুরআন মজীদ নাজিল করিয়াছেন। আর রাসূলে করীম (স) আল্লাহ্র সেই বিধানকে দৈনন্দিন কাজের মাধ্যমে বাস্তবায়িত করিয়াছেন। কুরআন অনুযায়ী রাসূলে করীম (স)-এর কাজ কুরানেরই বাস্তব ব্যাখ্যা। এই ব্যাখ্যা কুরানের ন্যায় চিরন্তন ও চির অনুসৃতব্য। খলীফা বা রাষ্ট্র চালক এই দুইটি বিধান অনুসরন করিয়া চলিতে বাধ্য। ইহাদের নির্ধারিত সীমা একবিন্দু লংঘন করার অধিকার কাহারও নাই। সাধারণ মানুষ একজন রাষ্ট্র চালককে মানিয়া চলিতে বাধ্য কেবলমাত্র এইজন্য যে, এই আনুগত্য রাষ্ট্র চালকের নিজস্ব গুণ বা অধিকারের জন্য নয়। ব্যক্তিগত গুণ-মর্যাদা বা অধিকারের কারণে কোন লোকই কাহাকেও মানিয়া চলিতে বাধ্য নয়। সে যদি আল্লাহ্র বিধান ও রাসূলের সুন্নাত অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা করে- আইন প্রণয়ন ও কার্যকর করে, তবে কেবলমাত্র এইজন্যই তাহাকে মানিয়া লইতে সকলে বাধ্য। কেননা এই আনুগত্য মূলত আলাহর আনুগত্য-আল্লাহ্র বিধান পালনের মাধ্যমে।প্রসঙ্গত স্মর্তব্য যে, আল্লাহ্র বিধান ও রাসূলের সুন্নাতের ব্যাখ্যাদানের একচেটিয়া অধিকার কাহারও নাই-এমন কি খলিফারও নয়। কুরআন-সুন্নাহর পারদর্শী যে কোন লোক উহা ব্যাখ্যাদানের অধিকারী। খলীফার এমন কোন ব্যাখ্যাও মানিয়া লওয়া যাইতে পারে না, যাহা আজ পর্যন্ত অন্য কোন বিশেষজ্ঞ কর্তৃকই স্বীকৃত হয় নাই। কাজেই কুরআন ও সুন্নাহর নামে নিজের মনগড়া বিধান চালু করা ইসলামী রাষ্ট্রশাসকের পক্ষে কোনক্রমেই সম্ভব হইতে পারে না। কেননা উহার অমূলকত্ত ও ভিত্তিহীনতা গোপন করার সাধ্য কাহারো নাই। খলীফার কুরআন-সুন্নাহ পরিপন্থী কোন নির্দেশ পালন করিতে কোন লোকই বাধ্য নয়। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক(রা)-এর উপরোদ্ধৃত ভাষণসমূহে এই কথাই উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষিত হইয়াছে। পরবর্তী খলিফাগণও নিজ নিজ ভাষায় এই কথার প্রতিধ্বনি বারবার করিয়াছে।
ইসলাম নির্ধারিত এই কর্মনীতি ও রাষ্ট্র শাসন পদ্ধতি পোপতন্ত্র তো নয়ই,ইহা গনতন্ত্র, রাজতন্ত্র বা স্বৈরতন্ত্রও নয়। কেননা পোপতন্ত্রে পাদ্রি-পুরোহিতরা আল্লাহ্র নামে নিজেদের মনগড়া শাসন চালায়। সে সম্পর্কে অন্য কাহারও কোন মন্তব্য করার অধিকার নাই। রাজতন্ত্র ও স্বৈরতন্ত্রে তো জনসাধারণ সকল প্রকার মানবিক ও মৌলিক অধিকার হইতেই সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত থাকিতে বাধ্য হয়। আর তথাকথিত গনতন্ত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে চলে দল-প্রধান বা দলের প্রভাবশালী লোকদের অথবা ক্ষমতা দখলকারী মুষ্টিমেয় কোটারীর চরম স্বেচ্ছাচারিতা। ইসলামী খিলাফতে আল্লাহ্র বিধান ও রাসূলের সুন্নাত মানিয়া চলার ব্যাপারে শাসক ও শাসিত, খলীফা ও জনগন সকলেই সমানভাবে বাধ্য;বরং যে ব্যক্তি এই মান্যতার দিক দিয়া অন্যদের তুলনায় অধিক অগ্রসর,সে-ই হয় এই রাষ্ট্রের খলীফা। খিলাফতের পদে নিযুক্ত হইয়া কোন ব্যক্তি কুরআন-সুন্নাহর বিধানও নিজ ইচ্চামত জারী করিতে পারে না। সেজন্য কুরআন-সুন্নাহ্ বিশেষজ্ঞদের সহিত পরামর্শ করিতে সে বাধ্য। কিন্তু পোপতন্ত্রে ধর্মযাজকরাই নিরংকুশ ক্ষমতার মালিক। তাহারা কাহারও সহিত কোন ব্যাপারে পরামর্শ করিতে বাধ্য নয়। তাহাদের কোন সিদ্ধান্ত সম্পর্কে কেহ প্রশ্ন তুলিতে পারে না; বরং তাহাদের কার্যাবলীর বিরূপ সমালোচনা করার পরিণতি অপঘাতে মৃত্যুবরণ ছাড়া আর কিছুই নয়। সাধারণ লোক সেখানে নিকৃষ্টতম গোলামের জীবন যাপন করিতে বাধ্য। পক্ষান্তরে ইসলামী খিলাফতে প্রত্যেকটি মানুষই স্বাধীন। সেখানে সমালোচনা করার শুধু অধিকারই দেওয়া হয় নাই, উহা প্রতিটি নাগরিকের দ্বীনী কর্তব্য বলিয়াও ঘোষিত হইয়াছে।
স্মর্তব্য যে, কুরআন ও সুন্নাহ ইসলামী খিলাফতের ভিত্তি বটে;কিন্তু উহাতে কেবলমাত্র মূলনীতি পেশ করা হইয়াছে। বিস্তারিত ও খুঁটিনাটি বিষয় উল্লেখ হইতে ইচ্ছা করিয়াই বিরত থাকা হইয়াছে। কোথাও তেমন কিছু উল্লেখিত হইয়া থাকিলেও অপরিহার্য ছিল বলিয়াই তাহা করা হইয়াছে। সেখানে তাহা উল্লেখিত না হইলে কুরআন ও সুন্নাতের বাস্তবায়ন সম্ভব হইত না। ইসলামী খিলাফতের যাবতীয় কাজ সেই সব মূলনীতির ভিত্তিতে সুসম্পন্ন করা হয়। সেসব মূলনীতির ভিত্তিতে বিস্তারিত ও খুঁটিনাটি বিষয় স্থির করা সর্বসাধারণ মানুষের দায়িত্ব এবং এই ব্যাপারে কাহারও একচেটিয়া অধিকার নাই। বস্তুতঃএই কারণেই ইসলামের জীবন ও রাষ্ট্রাদর্শ চিরন্তন ও শাশ্বত মূল্য লাভ করিতে পারিয়াছে।
কুরআন ও সুন্নাহ প্রদত্ত মূলনীতিসমূহ কালজয়ী।সর্বকালে সর্বাবস্থায় এবং সর্বদেশেই উহার ভিত্তিত আদর্শ মানব সমাজ গঠন করা শুধু সম্ভব নয় অবশ্য কর্তব্যও। সে সব মূলনীতি ছাড়া আদর্শ সমাজ গঠনের স্বপ্ন কোনদিনই বাস্তবায়িত হইতে পারেনা। মুসলমান যতদিন সেসব মূলনীতির ভিত্তিতে ব্যক্তি ও সমাজ গঠন করিয়াছে এবং বাস্তবে উহা অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে, ততদিন তাহারা যে ক্রমশঃধাপে ধাপে উন্নতির দিকে ধাবিত হইয়াছে, ইতিহাসই উহার অকাট্য প্রমাণ। কিন্তু যখনি সে মূলনীতিসমূহ ব্যক্তিগত ও জাতীয় পর্যায়ে পরিত্যক্ত হইয়াছে, উহার পরিপন্থী নীতি ও আদর্শ মানিয়া চলিতে শুরু করিয়াছে,তখনি তাহাদের পতন সূচিত হইয়াছে। বর্তমান বিশ্বের মুসলমানদের বাস্তব অবস্থা ইহারই জীবন্ত সাক্ষী।
আল্লাহ্র কিতাব ও রাসূলের সুন্নাতের ব্যাখ্যাদানের একচেটিয়া অধিকার বিশেষ এক শ্রেণীকে দেওয়া হইলে ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থাও ‘থিওক্রাটিক বা যাযকতন্ত্রও’ হইয়া যাইত; কিন্তু ইসলামে যে পৌরোহিত্যবাদ নাই, বিশেষ এক শ্রেণীর কোন একচেটিয়া কর্তৃত্বও ইহাতে স্বীকৃত নয়, একথা সর্বজনবিদিত। এখানে প্রত্যেক ব্যক্তিই স্বীয় যোগ্যতা বলে কুরআন ও সুন্নাহ অধ্যয়ন, চিন্তা-গবেষণা, বিচার-বিবেচনা এবং ফলাফল ও সিদ্ধান্ত গ্রহন অধিকারী। এই ব্যাপারে নির্বিশেষে সকলেরই সমান অধিকার রহিয়াছে। -শুধু তাহাই নয়,এই অধিকার প্রয়োগ করার জন্য সর্বসাধারণকে স্পষ্ট ভাষায় নির্দেশও দান করা হইয়াছে। কাজেই ইহার সহিত পোপতন্ত্রের(Papacy) যে দূরতম সম্পর্ক বা সাদৃশ্যও নাই, তাহা বলাই বাহুল্য।
ইসলামী খিলাফতে প্রত্যেক নাগরিককে শাসন কর্তৃপক্ষের প্রকাশ্য সমালোচনার অধিকার দেওয়া হইয়াছে। তাহাদের কাজকর্মের প্রতি তীক্ষ্ণ সজাগ দৃষ্টি রাখা এবং কুরআন ও সুনাহর আলোকে কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি গোচরীভূত হইলে সঙ্গে সঙ্গে উহার প্রতিবাদ করা ও উহার প্রতিকারের জন্য বাস্তব কর্মপন্থা গ্রহণ করা প্রতিটি নাগরিকের কর্তব্য বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। এই শাসন ব্যবস্থায় রাষ্ট্র পরিচালকগন নিজেদের জন্য কোন বিশেষ আইন রচনা করিয়া কোন বিশেষ অধিকার ভোগ করার সুযোগ পাইতে পারে না।খিলাফতে রাশেদার আমলে কুরআন ও সুন্নাহর বিধান শক্তভাবে পালন করার ফলে ইসলামী সমাজ এই ধরনের যাবতীয় অবাঞ্চিত ও কলঙ্কজনক আচরণ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র রহিয়াছে।তখন জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব এবং যাবতীয় অর্থ সম্পদ ছিল এক মহান আমানত। এই আমানতে বিন্দুমাত্র খিয়ানত করিলেও কিয়ামতের দিন কঠিন শাস্তি ভোগ করিতে হইবে, এই বিশ্বাস প্রত্যেকের মনে ইস্পাতের ন্যায় দৃঢ়মূল হইয়াছিল।
খিলাফতে রাশেদার চারজন খলীফাই জাতি ও রাষ্ট্রের অর্পিত আমানতসমূহ অত্যন্ত সযত্নে রক্ষণাবেক্ষণ করিয়াছেন,সে সবের যথাযথ ব্যয়-বণ্টন ও বিনিয়োগ নিশ্চিত করিয়াছেন এবং নিঃছিদ্র একনিষ্ঠতা, ঐকান্তিকতা, নিঃস্বার্থতা ও উচ্চমানের তাকওয়া-পরহেজগারীর বাস্তব নিদর্শন উপস্থাপিত করিয়াছেন। একালের লোকদের দৃষ্টিতে তাহা আজগুবী,অস্বাভাবিক ও অকল্পনীয় মনে হইলেও খিলাফতে রাশেদার ব্যাপারে উহাই ছিল বাস্তব সত্য। বস্তুতঃখিলাফত ও নেতৃত্ব তাঁহাদের মনে ও চরিত্রে বিন্দুমাত্র বিকৃতি ঘটাইতে পারে নাই; বরং তাহাদের তাকওয়ার মান ও মাত্রা পূর্বের তুলনায় অধিক বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছে।জনগণের ধন-সম্পদ হইতে অন্যায় ফায়দা লাভ,ক্ষমতার অপব্যবহার এবং নিজ বংশ ও আত্মীয়-স্বজনের জন্য বিশেষ সুযোগ-সুবিধা বিধানের চিন্তা তাঁহাদের মনে-মগজে মুহূর্তের তরেও স্থান লাভ করিতে পারে নাই। খিলাফতের কঠিন দায়িত্ব অর্পিত হওয়ার মুহূর্ত হইতেই তাঁহারা নিজেদের ব্যক্তিসত্তা ও বংশ-পরিবারবর্গকে বেমালুম ভুলিয়া গিয়া আল্লাহ্র দ্বীনের মর্যাদা রক্ষা এবং রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় কার্যাবলী সুসম্পাদনে নিজেদের সমগ্র শক্তি নিয়োজিত করিয়া ছিলেন।সর্বক্ষেত্রে ও সর্বব্যাপারে ইনসাফ ও পরিপূর্ণ সুবিচার প্রতিষ্ঠাই ছিল তাঁহাদের কর্মব্যস্ততার চরমতম লক্ষ্য। দুর্বল ও অভাবগ্রস্ত লোকদের সাহায্য দানের তুলনায় অধিক প্রিয় ব্যস্ততা তাঁহাদের নিকট আর কিছু ছিলনা।
যে রাষ্ট্র-ব্যবস্থা এই প্রকৃতির হয়, সেখানে স্বৈরাচার ও অত্যাচার-জুলুমের নাম-চিহ্ন পর্যন্ত থাকিতে পারে না। যে-রাষ্ট্রের কর্ণধার ও দায়িত্বশীল কর্মকর্তাবৃন্দ নিজদিগকে সাধারণ লোকের ঊর্ধ্বে মনে করেন না, মনে করেন সর্বসাধারণের খাদেম,উহাকে না পোপতন্ত্র বলা যাইতে পারে, না স্বৈরতন্ত্র। আধুনিক কালের তথাকথিত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের চরিত্রের সহিতও ইহার কোন সাদৃশ্য পাওয়া যাইতে পারে না। একথা সত্য যে, বর্তমানের ন্যায় সেকালে সাধারণ বয়স্ক ভোটাধিকারের(Adult suffrage) ভিত্তিতে খলীফা চতুষ্টয় নির্বাচিত হন নাই। যে অস্থির ও অশান্তিময় পরিস্থিতিতে এক এক ব্যক্তি খলীফা পদে বরিত হইয়াছেন, তাহাতে এই ধরনের নির্বাচনের কথা কল্পনাও করা যায় না। তৎসত্ত্বেও তদানীন্তন সমাজে তাঁহারাই যে সর্বাধিক আস্থাভাজন ব্যক্তি ছিলেন এবং ঐধরনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইলে তাঁহারাই যে নির্বাচিত হইতেন,ইহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ করা যায় না।খলীফা নির্বাচনে সাধারণতঃমুহাজির ও আনসার গোত্রের লোকেরাই অংশ গ্রহন করিতেন।আরবের তৎকালীন পরিস্থিতিতে অন্যান্য গোত্রের লোকদের সহিত এ ব্যাপারে পরামর্শ গ্রহণ করারও প্রয়োজন মনে করা হইত না তবে এই নির্বাচন গোত্রীয় গোপন যোগ-সাজশেরও পরিণতি ছিল না। আনসার ও মুহাজিররা কার্যতঃতদানীন্তন আরবের প্রায় সমস্ত গোত্রের মুসলিম জনতার প্রতিনিধিস্থানীয় ছিলেন।তাঁহাদের মতই ছিল সাধারণভাবে সমস্ত আরব মুসলিম জনতার রায়। রাসূলে করিম(স)-এর কিংবা পরবর্তী খলীফাদের এক একজনের আকস্মিক অন্তর্ধানের পর যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়, প্রত্যেক খলীফার নির্বাচনের মাধ্যমে তৎকালীন জরুরী পরিস্থিতিতে, অনতিবিলম্বে সেই শূন্যতা পূরণই অপরিহার্য এবং সর্বাধিক জরুরী কাজ হইয়া দেখা দিয়াছিল মুসলিম জাতির সম্মুখে।
এতৎসত্ত্বেও প্রত্যেক খলীফাই সমাজের সাধারণ আস্থাভাজন ব্যক্তিদের সহিত পরামর্শ করিয়াই রাষ্ট্র পরিচালনা করিয়াছেন। কেহই নিজের একক ও যুক্তিহীন মতের ভিত্তিতে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারসমূহে। খলীফাদের নির্বাচনে আত্মীয়তা কিংবা বংশমর্যাদা কোন কার্য-কারণ(Factor) হইয়া দেখা দিতে পারে নাই। তাঁহাদের কেহই এই পদের জন্য প্রার্থী হন নাই। এই পকদে নিযুক্ত হওয়ার লক্ষ্যে তাঁহাদের কেহ জনমত অনুকূলে আনার কোন অভিযান চালানোর আত্মনিয়োগ করেন নাই; বরং প্রত্যেকই নিজের পরিবর্তে অন্য কোন যোগ্যতর ব্যক্তিকে নির্বাচিত করাইবার জন্য চেষ্টা চালাইয়াছেন। এই পর্যায়ে প্রথম খলীফার নির্বাচন-কালীন কথাবার্তা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় চিরদিন উজ্জ্বল হইয়া থাকার অধিকারী। কোন কোন খলীফার নির্বাচনে প্রথম দিক দিয়া কিছুটা মত-বিরোধ দেখা দিলেও উত্তরকালে সেই মতবিরোধ বা বিরুদ্ধতার কোন অস্তিত্ব দেখা যায় নাই; বরং সকলেই অন্তর দিয়া সে নির্বাচনকে মানিয়া লইয়াছেন এবং নির্বাচিত খলীফার সহিত আন্তরিক সহযোগিতা করিয়াছেন। ইসলামী নির্বাচন নীতির এই বৈশিষ্ট্য তুলনাহীন।এই সমাজে স্থায়ী সরকারপক্ষ এবং স্থায়ী বিরোধীদল(Opposition) বলিতে কিছুই ছিলনা। এখানে সকলেই মিলিতভাবে ন্যায় ও সত্যের সমর্থক ও সহযোগিতাকারী এবং সকলেই অন্যায় ও ভুলনীতির বিরোধী, প্রতিবাদকারী। খলিফাগণ জনগণের অধিকার ও রাষ্ট্রের কল্যাণে পারস্পরিক পরামর্শের গুরুত্ব কত বেশি স্বীকার করিতেন, প্রথম খলীফার প্রাথমিক ভাষণের নিম্নোদ্ধৃত কথাগুলি হইতেই তাহা সুস্পষ্ট হইয়া উঠেঃ
আমি তোমাদের শাসক নিযুক্ত হইয়াছি, কিন্তু আমি তো তোমাদের তুলনায় উত্তম নহি। আমি যদি ন্যায়পথে চলি, তাহা হইলে আমার আনুগত্য ও অনুসরণ করিবে। কিন্তু ন্যায়ের পথ হইতে যদি আমার পদস্থলন হয় ও অন্যায় পথে চলিতে শুরু করি, তাহা হইলে তোমারা আমাকে ঠিক করিয়া দিবে, সঠিক পথে চালাইবে। আমি যত দিন আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের আনুগত্য করিতে থাকিব, ততদিন তোমারাও আমার আনুগত্য করিতে থাকিবে;কিন্তু আমিই যদি আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের নাফরমানী করি, তাহা হইলে আমার আনুগত্য করা তোমাদের কর্তব্য নয়।
শাসকের সহিত জনগণের গভীর ও নিবিড় সম্পর্ক এবং শাসককে সঠিক পথে পরিচালন ও সমালোচনার অধিকারের এইরূপ উদার-উদাত্ত স্বীকৃতির কোন দৃষ্টান্ত বর্তমান গনতন্ত্রবাদী যুগের তথাকথিত রাষ্ট্রসমূহের কোথাও দেখা যায় কি?খিলাফতে রাশেদার গোটা শাসন-কালই ছিল আধুনিক ভাষায় বলিতে গেলে নিতান্তই জরুরী অবস্থার যুগ(Emergency Period)ছিল। কিন্তু এই দীর্ঘ সময়ে জনগণের মৌলিক অধিকার কখনোই হরণ করা হয় নাই। শু’রা-পরামর্শ গ্রহণ ব্যবস্থা-সব সময়ই সুষ্ঠু রূপে কার্যকর রহিয়াছে। শু’রা-পার্লামেন্ট-ভাঙ্গিয়া দিয়া বিশেষ ক্ষমতা(Special power)নিজ হাতে গ্রহণ করার অধিকার খিলাফতের ভিত্তি –কুরআন ও সুন্নাহ-কাহাকেও কোন অবস্থায়ই দেয় নাই।
খলিফাগনের দৃষ্টিতে সব মুসলমানই ছিল সমান অধিকার ও সমান মর্যাদাসম্পন্ন;বৈষয়িক মান-মর্যাদার কারণে কেহই অন্যদের উপর প্রাধান্য ও অগ্রাধিকার লাভ করিতে পারিত না। প্রাক্তন মুর্তাদদের সম্পর্কে প্রথম খলীফা প্রথমে এই নির্দেশ জারী করিয়াছিলেন যে, সামরিক অভিযানসমূহে তাহাদিগকে যোগদান করিতে দেওয়া যাইবে না। কেননা তখনও তাহাদের ব্যাপারে পূর্ণ আস্থা ও নিশ্চিন্ততা লাভ করা যায় নাই। কিন্তু তাহাদের সম্পর্কে সন্দেহ ও সংশয় দূরীভূত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগকে ইসলামী মুজাহিদ বাহিনীর মধ্যে শামিল হওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়। ইরান অভিযানে তাহাদেরকে কাজে লাইগাবার জন্য হযরত উমর ফারুক(রা) কে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। ইহা খিলাফতে রাশেদার উদার,নীতিনিষ্ঠ ও বিদ্বেষমুক্ত দৃষ্টিকোণের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ছাড়া আর কিছুই নয়।
আরবের রাজনৈতিক একত্ব
প্রথম খলীফা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) তাঁহার অন্যান্য বিচক্ষণতা ও দূরদৃষ্টির সাহায্যে ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার ভিত্তিকে সুদৃঢ় করিয়া তোলেন। ইহার ফলে পরবর্তী খলিফাগণের পক্ষে সেই ভিত্তির উপর একটি বিশাল রাষ্ট্রপ্রাসাদ নির্মাণ করা এবং সমগ্র আরব উপদ্বীপকে একটি মাত্র রাজনৈতিক এককে(Unit) পরিণত করা খুবই সহজসাধ্য হয়। হযরত আবূ বকর (রা)-এর ক্ষমা,সহিষ্ণুতা ও ত্যাগ-তীতিক্ষামূলক নীতির দরুণ সমগ্র আরব উপদ্বীপকে ঐক্যবদ্ধ করার পথ সুগম হইয়াছিল। প্রথম দিকের সাময়িক বিশৃঙ্খলা প্রশমিত হওয়ার পর বিদ্রোহী-অপরাধী লোকেরা তাঁহার নিকট ক্ষমা লাভ করিয়া আন্তরিকতা সহকারে খিলাফতের আনুগত্য স্বীকার করে। শু’রা ব্যবস্থা সারাদেশের রাজনৈতিক ঐক্য ও সংহতিকে অধিকতর দৃঢ় ও শক্তিশালী করিয়া তোলে। ইহারই ফলে ইরাক ও সিরিয়া বিজয় সহজতর হইয়া যায়।
এই সময়কার আরব জনগণের চিন্তা-চেতনা ও মননশীলতা শু’রা ও গণ- অধিকারসম্পন্ন রাষ্ট্র ব্যবস্থার অনুকুল হইয়াছিল। ইসলামের অভ্যুদয় ও প্রকাশ আরব দেশে ঘটিয়াছিল। ইসলামী শরীয়াত-কুরআন ও সুন্নাহ-আরবী ভাষায় সন্নিবেশিত ছিল। সর্বশেষ রাসূল আরব দেশে প্রেরিত হইয়াছিলেন। আরব-গোত্রসমূহ বেদুঈন কিংবা নগরবাসী যাহাই হউক না কেন,স্বাধীনতা ও স্বরাজের জন্য ছিল অধীর ব্যাকুল। তাহাদের নিকট ইহাপেক্ষা অধিক প্রিয় ও আকর্ষণীয় জিনিস আর কিছুই ছিল না। মরুচারীদের মধ্যে সাম্য ও সমতার ভাবধারা পুরাপুরি সংক্রমিত হইয়াছিল। ইসলামী শিক্ষা ও প্রশিক্ষন এই ভাবধারাকে অধিক স্বচ্ছতা ও পরিপক্কতা দান করে। কেননা ইসলামই প্রকৃত সাম্য ও সমতার পূর্ণাঙ্গ আদর্শ উপস্থাপন করিয়াছে। কুরআন মজীদ এই সাম্য ও সমতার বাণী উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছে। কুরআনের ঘোষণানুযায়ী বংশ মর্যাদা বা ধন-সম্পদের আধিক্য ও প্রাচুর্যের নয়, আল্লাহ্র ভয় (তাকওয়া) ও আল্লাহ্র দ্বীন পালনই মর্যাদা ও সম্মানের মানদণ্ড। বর্তমান যুগে সর্বত্র গণতন্ত্রের জয়ধ্বনি উচ্চারিত। কিন্তু প্রকৃত মানবিক মূল্যবোধ ও ভাবধারা খিলাফতে রাশেদার আমলেই সমুজ্জ্বল প্রতিভাত হইয়াছে। মানবতা, ভ্রাতৃত্ব,প্রেম-প্রীতি,স্বাধীনতা ও সাম্য বর্তমান গণতন্ত্রের স্ফীত কণ্ঠে সমুচ্চারিত। কিন্তু ইহার প্রকৃত বাস্তবায়ন কেবলমাত্র খিলাফতে রাশেদার আমলের প্রতিটি ক্ষেত্রেই দ্রষ্টব্য। ইসলামের পবিত্র শিক্ষা প্রতিটি মু’মিনকে অপর মু’মিনের একনিষ্ঠ ‘ভাই’ ও সত্যিকার কল্যাণকামী বানাইয়া দিয়াছিল। কোন লোক নিজের জন্য যাহা পছন্দ করে, অপর ভাইয়ের জন্য তাহাই পছন্দ না করা পর্যন্ত ঈমানদার হইতে পারে না-রাসূলে করীম(স)-এর ঘোষণা একটা সাধারণ ও মূল্যহীন কণ্ঠধ্বনি ছিল না। ইহা ছিল মানবাধিকারের সপক্ষে এক ঐতিহাসিক ঘোষণা। এই গভীর বুদ্ধিসম্মত ঘোষণাকে বাস্তবায়িত করিয়া তোলা না হইলে কোন রাষ্ট্রই প্রকৃত জনকল্যাণমুখী চরিত্র লাভ করিতে পারে না এবং এই ঘোষণাকে আলোক-মশালরূপে গ্রহণ করিয়া সাধারণ জনগণকে পরস্পরের কল্যাণকামী ও সহানুভূতিশীল রূপে গড়িয়া না তোলা পর্যন্ত কোন গণকল্যাণকামী রাষ্ট্রের পক্ষে বিন্দুমাত্র সাফল্য লাভ অসম্ভব। বস্তুতঃবর্তমান গণতন্ত্রবাদী রাষ্ট্রসমূহের চরম হাস্যকর ব্যর্থতা এবং খিলাফতে রাশেদার পূর্ণ সাফল্যের মূলে এই তত্ত্বই নিহিত। বলা নিষ্প্রয়োজন, রাসূলে করীম(স)-এর এবম্বিধ মহামূল্য বাণীসমূহকে ভিত্তি করিয়াই ইসলামই রাষ্ট্রের বিরাট প্রাসাদ রচনা করা হযরত আবূ বকর (রা)-এর পক্ষে সম্ভবপর হইয়াছিল। আর এই বানীসমূহের পূর্ণ অনুসরণের মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালনা করিয়া সমকালীন বিশ্বরাষ্ট্র-দর্শনের সম্পূর্ণ বিপরীত-খিলাফতে রাশেদার মহান ব্যবস্থা পরিচালনা করিয়া সমগ্র বিশ্বকে বিস্মিত-বিমুগ্ধ করা পরবর্তী খলিফাত্রয়ের পক্ষে সম্ভবপর হইয়াছিল।
ইসলামী রাষ্ট্র-নীতির অন্তর্নিহিত শক্তি
খিলাফতে রাশেদার রাষ্ট্র-ব্যবস্থা কেবলমাত্র আরব উপদ্বীপ নামক ভূখণ্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ হইয়া থাকে নাই। উহা সে ভূ-খণ্ডের সীমা অতিক্রম করিয়া অত্যল্প কালের মধ্যেই বাঁধ-ভাঙা বন্যার মত চতুর্দিকের দূর দূর-অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত ও সম্প্রসারিত হইয়া পড়ে। কিন্তু একটি আরব রাষ্ট্রের পক্ষে বিশাল অনারব এলাকায় সম্প্রসারিত হওয়া কি নিছক কতিপয় সামরিক অভিযানের পরিণতি ছিল? ইতিহাসের ইহা একটি জটিল প্রশ্ন। এই প্রশ্নের জবাব বিশ্লেষণ একান্তই আবশ্যক।
বস্তুতঃ ইসলাম এক সর্বজনীন বিপ্লবী বাণী লইয়া দুনিয়ার বুকে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। সে বানীর ব্যাপক প্রচার ও প্রসার এবং উহার অনুকূলে নীরব জনমত গড়িয়া উঠাই ইসলামের জয়জয়কার ও দেশের পর দেশ ইসলামের পতাকাতলে আশ্রয় লওয়ার এক বিস্ময়কর ইতিহাস সৃষ্টি করিয়াছে। এই বিজয়সমূহকে বৃক্ষের বৃন্ত-সংলগ্ন পাকা ফল এক টোকায় পাড়িয়া লওয়া কিংবা সদ্য-ভূমিষ্ঠ সন্তানের নাড়ি কাটিয়া দেওয়ার সহিত তুলনীয়। ইসলামী আদর্শবাদ প্রথমে ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়াছে, পথ সুগম করিয়া লইয়াছে এবং পরিণামে ইসলামী বিপ্লব সৃষ্টির সব বাধা-প্রতিবন্ধকতা দূর হইয়া গিয়াছে। এই ভাবেই মুসলমানদের পক্ষে দুনিয়ার বিশাল অঞ্চলে ইসলামী রাষ্ট্রকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর গড়িয়া তোলা সম্ভবপর হইয়াছিল।
ইসলামী ইতিহাসের প্রাথমিক পর্যায় সম্পর্কে অবহিত কোন ব্যক্তির নিকটই একথা গোপন থাকিতে পারে না যে, ইসলামের মুজাহিদদের সাফল্য কোন সাময়িক বা দুর্ঘটনামূলক ব্যাপার ছিল না। এই বিজয় ছিল ঘটনা-প্রবাহের এক দীর্ঘ ধারাবাহিকতার অবিচ্ছিন্ন অংশ। মূলতঃ ইসলাম দুনিয়ায় যে বিপ্লব সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহা ছিল অবধারিত। কেননা ইসলামের মূল আদর্শেই বিপ্লবের অগ্নিবাস্প নিহিত রহিয়াছে। এই দুর্জয় শক্তির বিস্ফোরিত হওয়া ছিল অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার।
ইসলামের মূল আকীদা- এক আল্লাহ্ ছাড়া আর কাহাকেও মানি না, ভায় করিনা, অন্য কাহারও নিকট একবিন্দু নতি স্বীকার করি না এবং রাসূলে করীম (স)ই আল্লাহ্র প্রেরিত রাসূল, আমাদের একমাত্র পথনির্দেশক- এই দৃঢ় প্রত্যয়ই ইসলামকে এ বিশ্ববিজয়ী শক্তি দান করিয়াছে। আকীদা-বিশ্বাসের এই বলিষ্ঠতাই সাধারণ মানুষকে বিপ্লবী বানাইয়া দিয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে মন ও মানসের এই স্বাধীনতা ইসলামের এক বিরাট অবদান। সেই সঙ্গে ধর্ম ও মতাদর্শের ব্যাপারে কোনরূপ বলপ্রয়োগ ছিল খিলাফতে রাশেদার সম্পূর্ণ নীতিবিরুদ্ধ। ইসলাম গ্রহণের জন্য সারা দুনিয়ার মানুষকে আহ্বান জানানো হইয়াছে বটে; কিন্তু নিজের ধর্মবিশ্বাস পরিবর্তন করার জন্য ইসলাম কাহাকেও বাধ্য করে না। তবে ইসলামের আদর্শ সম্পর্কে লোকেরা গুরুত্ব সহকারে চিন্তা-বিবেচনা করিবে, দুনিয়ার অন্যান্য ধর্ম ও মতাদর্শের সহিত উহার তুলনামূলক আলোচনা ও অধ্যয়ন করিয়া উহার বৈশিষ্ট্য নিরপেক্ষভাবে স্বীকার করিবে, ইসলামের ইহা এক বলিষ্ঠ আশাও বটে। কেননা তাহা হইলে ইহা গ্রহণ না করিয়া কেহ যে থাকিতে পারিবে না, এই সম্পর্কে ইসলাম নিঃসন্দেহ। বস্তুতঃইসলাম মানব প্রকৃতির সহিত পুরাপুরি সামঞ্জস্যশীল এক পূর্ণাঙ্গ জীবন-বিধান। সুস্থ বিবেক-বুদ্ধি পূর্ণাঙ্গ জীবনাদর্শ হিসেবে একমাত্র ইসলামকেই গ্রহণ করিতে পারে, এই বিষয়ে ইসলামের কোন সংশয় নাই।
ইসলামের মুক্তি ও স্বাধীনতার এই বিপ্লবী বাণীই দুনিয়ার অন্যান্য ধর্ম ও মতাদর্শের পক্ষে কঠিন চ্যালেঞ্জ হইয়া দেখা দিয়াছে। কেননা আকীদা-বিশ্বাস ও কর্মনীতি গ্রহণের স্বাধীনতা দেওয়া হইলে ইসলামের নির্ভুল ও পূর্ণাঙ্গ আদর্শই যে সর্ব শ্রেণীর মানুষকে প্রবলভাবে আকৃষ্ট করিবে, মানুষ নিজের ভুল ধর্ম ও মতাদর্শ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ত্যাগ করিবে, ইহা ইসলামী দাওয়াত ও আন্দোলনের এক পরীক্ষিত সত্য। আর ইহার পরে দুনিয়ার অপরাপর ধর্ম ও মতাদর্শের যে অপমৃত্যু ঘটিবে, তাহা সন্দেহাতীত। ইসলামের পূর্ণাঙ্গ আদর্শ প্রচারে দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে যে বাধার সৃষ্টি করা হয়, উহার মূলে একমাত্র এই কারণই নিহিত রহিয়াছে।
ইসলাম মনের স্বাধীনতা(Freedom of mind)-র যে বিপ্লবী আদর্শ দুনিয়ার সম্মুখে পেশ করিয়াছে, খিলাফতে রাশেদার আমলে তাহা পুরাপুরি কার্যকর ও বাস্তবায়িত হইয়াছে। এই আমলে বহুদেশ অধিকৃত হইয়াছে বহু জনপদ ইসলামের অধীনতা মানিয়া লইয়াছে; কিন্তু একজন লোককেও জোরপূর্বক স্বীয় ধর্মমত পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করা হয় নাই। কাহাকেও সে জন্য প্রলোভিত করা হয় নাই। যে লোক স্বেচ্ছায় ও সোৎসাহে ইসলাম কবুল করিয়াছে, সে অন্যান্য সব মুসলমানের মতই সমান মর্যাদা ও অধিকার লাভ করিয়াছে। পক্ষান্তরে যে লোক স্বীয় পূর্বত্ন ধর্ম ও মতাদর্শে অবিচল থাকিতে চাহিয়াছে, তাহাকেও সেইরূপ থাকিবার জন্য পূর্ণ অধিকার দেওয়া হইয়াছে। সে যাহাতে নিজস্ব ধর্ম পালনের সঙ্গে সঙ্গে স্বীয় ধন-মান ও প্রানের নিরাপত্তা সহকারে বসবাস করিতে পারে, সেজন্য ইসলামী খিলাফত পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে। বিনিময়ে তাহাদের সামর্থ্যনুযায়ী একটা বিশেষ ‘কর’(Tax) গ্রহণ করা হইয়াছে। এই কর কোন রূপ জরিমানা ছিল না। তাহাদের সার্বিক নিরাপত্তার নিশ্চিত করার জন্য রাষ্ট্রকে যে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইত, ইহা ছিল সে ব্যাপারে এক বিশেষ ধরনের চাঁদা। ইহাকে আরবী পরিভাষায় ‘জিজিয়া’বলা হয়। এই শব্দের অর্থঃ বদলা বা বিনিময়। আর বস্তুতঃ ইহা ছিল তাহার ধর্ম,ধন-মাল, মান-সম্ভ্রম ও প্রাণের নিরাপত্তা বিধানের জন্য খিলাফত কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থার বিনিময় মূল্য মাত্র। যেখানে এই নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণের দায়িত্ব পালনে খিলাফত অক্ষম হইয়াচে,সেখানে ইহা গ্রহণ শুধু বন্ধই করা হয় নাই,পূর্ব গৃহীত করও ফেরত দেওয়া হইয়াছে। ইসলামী ইতিহাসের পৃষ্ঠায় একথা সুস্পষ্টভাবে ও স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে।
বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর প্রতি বিশ্বাসী ও তাঁহার জন্য উৎসর্গীকৃত প্রাণ লোকদের হাতে প্রতিষ্ঠিত এই রাষ্ট্র ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপিত ছিল ব্যক্তি স্বাধীনতা, মৌলিক মানবীয় অধিকার, নির্বিশেষে সাম্য ও ভ্রাতৃসুলভ প্রেম-প্রীতি ও ভালোবাসার উন্নত নীতিমালা ও আদর্শের উপর। ইহা ছিল রোমান রাজতন্ত্রবাদের সম্পূর্ণ বিপরীত ধরনের এক রাষ্ট্র ব্যবস্থা। অন্যদিকে সাধারণ মানবীয় কল্যাণের দৃষ্টিতে আধুনিকতম তথাকথিত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থাও উহার তুলনায় অত্যন্ত দীন-হীন। বস্তুত অনারব লোকদিগকে আরবের অধীন-অনুগত বানানো খিলাফতে রাশেদার কোন লক্ষ্য ছিল না। তদানীন্তন রোমান ও পারসিকদের নিকৃষ্টতম দাসত্ব হইতে মুক্ত করিয়া আরবদের দাসত্ব নিগড়ে উহাদিগকে বন্দী করাও ছিল না উহার উদ্দেশ্য; বরং মানুষকে সর্বপ্রকার মানবিক ও বৈষয়িক গোলামী হইতে পরিপূর্ণ মুক্তিদান, একমাত্র সৃষ্টিকর্তার বন্দেগী ও রাসূলের নেতৃত্ব স্বীকার করিয়া দ্বীন-ইসলামের মহান বিধান অনুযায়ী সম্পূর্ণ স্বাধীন পরিবেশে জীবন যাপন ও বিকাশ-বর্ধনের অবাধ-উদার ও উন্মুক্ত সুযোগ করিয়া দেওয়াই ছিল উহার যাবতীয় চেষ্টা-প্রচেষ্টা ও সাধনা-সংগ্রামের চরমতম লক্ষ্য। ইসলামের সুমহান আদর্শে ঐকান্তিক বিশ্বাস এবং পরস্পরের গভীর ভ্রাতৃত্ব ও একনিষ্ঠ প্রেম-প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হওয়াই ছিল উহার একমাত্র উপায়। খিলাফতে রাশেদার আমলে বিজয়ী ও বিজিত বলিতে কোন শ্রেণী-বিভেদ ছিল না। সর্বশ্রেণী- সকল স্তর ও পর্যায়ের মানুষের সেখানে পুরাপুরি সমান অধিকার ও মর্যাদালাভে ধন্য হইয়াছিল। ভাষা,গোত্র ও অঞ্চলের ভিত্তিতে তাহাদের মধ্যে কোন পার্থক্য ও তারতম্য ছিল না। এমন কি ইরাক ও সিরিয়ার অমুসলিম এবং নাজরান ও আরবের অন্যান্য এলাকার খৃষ্টানদের মধ্যেও কোনরূপ পার্থক্য সৃষ্টি হইতে দেওয়া হয় নাই। মুসলমানগণ তাহাদের মধ্যে ইসলাম প্রচারের কাজ করিতেন বটে; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও যাহারা নিজেদের পৈতৃক ধর্মে অবিচল থাকিতে চাহিত, তাহাদিগকে সেইরূপ থাকারই পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছিল। খিলাফতে রাশেদার আমলে ধর্ম গ্রহণের ব্যাপারে কুরআনের নিম্নোদ্ধৃত ঘোষণাদ্বয় পুরামাত্রায় কার্যকর ছিলঃ
******(আরবী)
দ্বীন ও ধর্মের ব্যাপারে কোনরূপ বল প্রয়োগ বা জোরজবরদস্তির স্থান নেই।
যে লোক হেদায়েত গ্রহণ করে, উহার কল্যাণে সে নিজেই লাভ করিবে। আর যে লোক পথভ্রষ্ট হইয়া থাকিতে চাহে, উহার ক্ষতি ও অকল্যাণ তাহাকেই ভোগ করিতে হইবে। হে রাসূল আপনি লোকদিগকে বলিয়া দিন,তোমাদের পর্যন্ত সত্যের বাণী পৌঁছাইয়া দেওয়াই আমার কাজ; গ্রহণ করা বা না করা তোমাদের নিজেদের দায়িত্ব। তোমাদের হেদায়েত বা গুমরাহীর কোন দায়িত্ব আমার উপর বর্তায় না।
খিলাফতে রাশেদার আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা
খিলাফতে রাশেদার রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় ইসলামী সমাজ-সভ্যতা ও কৃষ্টি-তামাদ্দুনের পূর্ণ বাস্তবায়ন নিস্পন্ন হইয়াছিল।ইহা একাধারে ছিল দ্বীন-ভিত্তিক ও বৈষয়িক উন্নয়নের একমাত্র নিয়ামক রাষ্ট্র। দ্বীন-ইসলামের উপরই উহার ভিত্তি স্থাপিত ছিল এবং কুরআনের অকাট্য মূলনীতি ও রাসূলে করীম(স)- এর সুন্নাত অনুযায়ী মানবতার সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ সাধনই ছিল উহার যাবতীয় চেষ্টা-সাধনার একমাত্র লক্ষ্য।
খিলাফতে রাশেদার আমলে কুরআন মজীদ ও সুন্নাতে রাসূল মুতাবিকই যাবতীয় আইন-কানুন প্রণয়ন করা হইত। খুলাফায়ে রাশেদুন যদি এমন কোন সমস্যা বা জিজ্ঞাসার সম্মুখীন হইতেন,যাহার প্রত্যক্ষ মীমাংসা কুরআন ও হাদীস হইতে লাভ করিতে পারিতেন না, তাহা হইলে নবী করীম(স)-এর কার্যাবলীর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সম্মুখে রাখিয়া উত্তমভাবে উহার মিমাংসা করিয়া লইতেন এবং কোন দিক দিয়াই কুরআন ও সুন্নাতে রাসূলের মৌলিক আদর্শ লংঘিত হইতে দিতেন না।
ইসলামের মৌলিক বিধান অনুসারে গোটা উম্মতে মুসলিমা খলীফাদের আনুগত্য স্বীকার করিয়া চলিতে বাধ্য ছিল। কিন্তু সেই সঙ্গে এই মূলনীতিও সর্বাপেক্ষা সমর্থিত ছিল যে, আল্লাহ্ ও রাসূলের হুকুম-বিধানের বিরুদ্ধতা করিয়া কোন খলীফা বা রাষ্ট্রকর্তার আনুগত্য করা যাইতে পারে না। কুরআন-হাদীসের মূল সূত্র হইতে বাস্তব ও ব্যবহারিক জীবনের খুঁটিনাটি আইন-কানুন প্রনয়নের অধিকারের ক্ষেত্রে খলীফার কোন প্রাধান্য, বিশিষ্টতা ও অগ্রাধিকার স্বীকৃত ছিল না। অনেক ক্ষেত্রে খলীফা বরং অন্যান্য সাহাবীদের নিকট কুরআন-হাদীস-ভিত্তিক রায় বা পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতেন। এই ব্যাপারে খলীফাদের সঙ্গে দ্বিমত হওয়ারও পূর্ণ অধিকার ছিল। শুধু তাহাই নয়,খলীফাদের রায়ের ভুল-ভ্রান্তি ধরাইয়া দেওয়া এবং তাঁহাদের প্রকাশ্য সমালোচনা করার সাধারণ অধিকারও সর্বতভাবে স্বীকৃত ছিল।
জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত রায় বা সম্মতি অনুযায়ী খলীফা নির্বাচিত হইতেন। জোরপূর্বক কিংবা বংশানুক্রমিক ধারা অনুযায়ী খলীফার পদ দখল করা শুধু ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থারই খেলাফ নহে, ইসলামী বিধানের দৃষ্টিতে উহা মারাত্মক অপরাধও বটে। খুলাফায়ে রাশেদুনের মধ্যে বাদশাহী শান-শওকাত কিংবা ডিকটেটরী স্বৈরতন্ত্রের কোন অস্তিত্তই বর্তমান ছিল না। তাঁহারা নিজদিগকে নাগরিকদের সমপর্যায়ভুক্ত মনে করিতেন। একমাত্র খিলাফত ভিন্ন অন্য কোন দিক দিয়াই তাঁহাদের ও সাধারণ জনগণের মধ্যে একবিন্দু পার্থক্য ছিল না। খলীফার দরবারে সরকারী কর্মচারী ও জনসাধারণের অবাধ যাতায়াত ছিল এবং এই ব্যাপারে কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতার অবকাশ ছিল না। এই কারণে জনগণের সাধারণ অবস্থা ও অভাব-অভিযোগ সম্পর্কে প্রত্যক্ষভাবে ওয়াকিফহাল হওয়া এবং কোন প্রকার দীর্ঘসূত্রিতা ব্যতিরেকেই উহার প্রতিকার করা তাঁহাদের পক্ষে অত্যন্ত সহজ ছিল।এই কারণেই এ কথা উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করা যাইতে পারে যে, খিলাফতে রাশেদাই হইতেছে বিশ্ব- ইতিহাসে একমাত্র ও সর্বপ্রথম রাষ্ট্র, যেখানে প্রকৃত গণ-অধিকার পুরাপুরিভাবেই রক্ষিত হইয়াছে।
বিচার বিভাগ
খুলাফায়ে রাশেদুনের আমলে বিবদমান দুইপক্ষের মধ্যে ইনসাফ বা ন্যায় বিচার নিশ্চিত করা খলীফার অন্যতম দায়িত্ব মনে করা হইত। এইজন্য প্রথম দিকে তাঁহারা প্রায় সব বিচারকার্য নিজেরাই সম্পন্ন করিতেন। অবশ্য দূরবর্তী স্থানসমূহের জন্য নিজেদের তরফ হইতে প্রতিনিধি নিযুক্ত করিতেন। প্রথম খলীফার আমলে প্রত্যেক শহরের জন্য নিযুক্ত শাসনকর্তাই বিচার কার্য আঞ্জাম দিতেন। কিন্তু দ্বিতীয় খলীফা তাঁহার খিলাফত আমলে বিচার বিভাগকে সম্পূর্ণ স্বাধীন ও স্বতন্ত্র করিয়া দিয়াছিলেন। এইজন্য প্রত্যেক শহরেই স্বতন্ত্র মর্যাদাসম্পন্ন বিচারপতি বা কাজী নিয়োগ করা হইয়াছিল। বিচার বিভাগ প্রসাশন বিভাগের কর্তৃত্ব হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও স্বাধীন মর্যাদাসম্পন্ন ছিল। বিচারপতি রায়দানের ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিলেন। খলীফার পক্ষ হইতে তাঁহাদিগকে এই নির্দেশ দান করা হইত যে, তাঁহারা বিচারে যে রায়ই দান করিবেন, তাহা যেন সর্বতোভাবে কুরআন ও সুন্নাতে-রাসূলের ভিত্তিতে সম্পন্ন হয়। কোন দিক দিয়াই যেন উহা লংঘন করা না হয়। সংশ্লিষ্ট এলাকার শাসনকর্তা বিচারপতির উপর কোন প্রকার প্রভাব বিস্তার কিংবা প্রভুত্ব খাটাইতে পারিতেন না। কাজী বা বিচারপতি সরাসরি খলীফা কর্তৃত্ব নিযুক্ত হইতেন। সংশ্লিষ্ট শহরের শাসনকর্তাকেও অনেক সময় বিচারপতি নিয়োগের ইখতিয়ার দান করা হইত; কিন্তু তাহা ছাড়া বিচারপতি নিয়োগের ব্যাপারে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা হইত। চতুর্থ খলীফার প্রদত্ত একখানি নিয়োগপত্রের নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতে ইহার বাস্তব প্রমাণ পাওয়া যায়। লোকদের মামলা –মুকাদ্দমা নিস্পত্তি করার জন্য এমন সম্মানিত ব্যক্তিদের নিয়োগ কর,যাহাদের রায় জনগণ অকুণ্ঠিত চিত্তে মানিয়া লইবে এবং কেহ উহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার কোন সাহস বা প্রয়োজন বোধ করিবে না। তাঁহারা হইবেন সকল প্রকার লোভ-লালসা ও মোহ-মাৎসর্য হইতে পবিত্র। তাঁহারা কাহারো বিশেষ মর্যাদার কারণে সন্ত্রস্ত ও প্রভাবান্বিত হইবেন না। সকল ব্যাপারেই তাঁহাদিগকে গভীর-সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বশীল হইতে হইবে। সন্দেহ-সংশয়পূর্ণ ব্যাপারে তাঁহারা অত্যন্ত সতর্ক হইবেন। পক্ষদ্বয়ের উপস্থাপিত যুক্তিপূর্ণ প্রমাণ ও সাক্ষ্য সন্দর্শনে কিছুমাত্র ঘাবড়াইয়া যাইবেন না, প্রতিটি ব্যাপারের গভীর তলদেশে পৌঁছিবার জন্য পরিপূর্ণ সতর্কতা ও চিন্তা-গবেষণা সহকারে কাজ করিবেন। এইভাবে তাঁহারা কোন চূরান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়া গেলে তাহা পুরাপুরি দৃঢ়তা সহকারে কার্যকর করিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হইবেন না। কোন প্রকার সুপারিশ ও কোনরূপ পদ-মর্যাদাকেই তাঁহারা ফয়সালা কার্যকর করার পথে বাধা হইয়া দাঁড়াইতে দিবেন না। যদিও এই ধরনের লোকদের সংখ্যা বেশী হয় না কখনো, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও বিচারপতিকে অবশ্যই উল্লেখিত গুণে ভূষিত হইতে হইবে। তোমরা যখন কাহাকেও বিচারপতি নিযুক্ত করিবে, তখন তাহার যথেষ্ট পরিমানে বেতন ধার্য করিবে; তাহা হইলে তাহার জীবনযাত্রা নির্বাহের দাবি তাহাকে ঘুষ লইতে বাধ্য করিবে না। উপরন্তু তোমাদের মন-মানস ও সমাজ-সম্মেলনে তাহার মর্যাদা উন্নত হওয়া বাঞ্ছনীয়, যেন তাহার বিরুদ্ধে প্রচারণা চালাইবার সাহস কাহারো না হয়।
বিচারকগণ ছাড়াও প্রত্যেক শহরেই ইসলামী আইন সম্পর্কে বিশেষ দক্ষতাসম্পন্ন একটি জনগোষ্টী সব সময়ই মওজুদ থাকিত। কোন ব্যাপারে বিচারকদের অসুবিধা বা সমস্যা দেখা দিলে ইহাদের নিকট হইতে সাহায্য গ্রহণ করা হইত।
এই সময় নবী করীম(স)-এর হাদীসসমূহ গ্রন্থাবদ্ধ ছিল না, তাহা ছিল লোকদের স্মৃতিপটে রক্ষিত। কেহ একটি হাদীস জানিত আর কাহারো স্মরণ ছিল অন্য একটি হাদীস। সমস্ত হাদীস এককভাবে বিশেষ কাহারো স্মরণ ছিল না আর ইহাই ছিল সেকালের একটি কঠিন সমস্যা। বিচারকদের সম্মুখে উপস্থিত ব্যাপারের মীমাংসা করার জন্য কোন হাদীসের প্রয়োজন হিলে তাঁহারা বিভিন্ন লোকের নিকট জিজ্ঞাসা করিতেন এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে রাসূলে করীম(স)-এর নির্দেশ বা কর্মনীতি জানিতে চেষ্টা করিতেন। ফলে তাঁহারা রাসূলের যে হাদীসি পাইতেন, সেই অনুযায়ী বিচার-ফয়সালা করিতেন; কিন্তু সুনির্দিষ্ট কোন হাদীস পাওয়া না গেলে ইসলামের সামগ্রিক ব্যবস্থা ও উহার ধারাকে সম্মুখে রাখিয়া তাঁহারা ইজতিহাদ করিতেন। এই কারণে অনেক সময় কোন নির্দিষ্ট ব্যাপারে বিচারকের বিভিন্ন প্রকার হইত। বিচারকদের ফয়সালাসমূহ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখার তখনো শুরু হয় নাই। ফলে পরবর্তীকালের লোকেরা উহা হইতে কিছুমাত্র ফায়দা লাভ করিবার সুযোগ পাইত না।
এই যুগের যাবতীয় বিচার কার্য কেবলমাত্র ইজতিহাদের উপর নির্ভরশীল ছিল বলিয়া কাহারো কাহারো মনে প্রশ্ন জাগিতে পারে; কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার তাহা নহে। কেবলমাত্র শরীয়াতের খুঁটিনাটি আইন জানিবার ও যুগের বিশেষ অবস্থা ও ঘটনার উপর উহাকে প্রয়োগ করার ব্যাপারেই ইজতিহাদ-নীতি ব্যবহার করা হইত। স্মর্তব্য যে,ইসলামী আইনসমূহ ছিল কতকগুলি মূলনীতির সমষ্টি; উহার খুঁটিনাটি বিধান তখনো রচিত হয় নাই। বস্তুত চিরকাল ও সমগ্র মানবতার জন্য প্রদত্ত আইন-বিধান এইরূপ হওয়াই স্বাভাবিক। কালের প্রতিটি পর্যায়ে ও পৃথিবীর প্রতিটি অঞ্চলেই উহার বাস্তব প্রয়োগ কেবলমাত্র এই ভাবেই সম্ভব ও সহজ হইতে পারে।
বিচারক নিয়োগের পরও জনগণের ঝগড়া-বিবাদ মীমাংসা করার ব্যাপারে খলীফাদের প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহনে কোন বাধা ছিল না; বরং অনেক ক্ষেত্রে তাঁহারা নিজেরাই অনেক ঝগড়া-বিবাদ মীমাংসা করিতেন। সেইসব ক্ষেত্রে নিযুক্ত বিচারকগন শুধু খলীফাদের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করিতেন মাত্র।
দেশরক্ষা বিভাগ
খিলাফত আমলে যুদ্ধ বা সৈন্যবাহিনী পরিচালনা করার মূল ক্ষমতা খলীফার হস্তেই নিবদ্ধ থাকিত। কেননা নবী করীম (স)-এর জামানায়ও এই রীতিই কার্যকর ছিল। তিনি নিজেই সৈন্যবাহিনীর নেতৃত্ব দিতেন। কিন্তু পরবর্তীকালে শাসন পরিধি যখন বিশালতর হইতে লাগিল, তখন খলীফাগণ সর্বশ্রেষ্ঠ বীর ও যোদ্ধা হওয়া সত্ত্বেও পৃথকভাবে সেনাধ্যক্ষের নিযুক্তি শুরু হইল। তাহাকে মানিয়া চলা স্বয়ং খলীফাকে মানিয়া চলার মতই অবশ্যই কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। যুদ্ধের অবসান হইলে সামরিক ব্যাপারসমূহ পর্যবেক্ষণ ও ভবিষ্যতের জন্য তাহাদিগকে ট্রেনিং দান করিই হইত সেনাধ্যক্ষদের একমাত্র কাজ।
হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)- এর খিলাফত আমলে সমগ্র সৈন্যবাহিনী অবৈতনিক ও স্বেচ্ছামূলক ছিল। কোন রেজিস্ট্রি বহিতে তাহাদের নাম লিপিবদ্ধ ছিল না। হযরত উমর ফারুক (রা)-এর খিলাফত কালেই সৈন্য বিভাগ সুষ্ঠু ও সুসংবদ্ধভাবে গঠিত হয় ও প্রতিটি সৈনিকের নাম রেজিস্ট্রিভুক্ত হয়। ইহার ফলে সৈন্যবাহিনীতে শৃঙ্খলা স্থাপিত হয়। কোন সৈনিক পলায়ন করিলে কিংবা পশ্চাতে থাকিয়া গেলে অতি সহজেই তাহা ধরা পড়িত। পলাতক সৈনিকদের জন্য তখন একটি বিশেষ ধরনের শাস্তি নির্দিষ্ট ছিল। পলাতকের নিজ মহল্লার মসজিদে তাহার নাম প্রকাশ ও প্রচার করিয়া ঘোষণা করা হইত যে,এই ব্যক্তি জিহাদের ময়দান হইতে পলাইয়া আসিয়াছে;আল্লাহ্র পথে আত্মদান করার ব্যাপারে সে কুণ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছে। বস্তুতঃ এতটুকু ভৎসনা আরবের জন্য মৃত্যুদণ্ড অপেক্ষাও সাংঘাতিক ছিল। কেননা সমগ্র বিশ্ব-জাতির মাঝে আরবদের যে অতুলনীয় বীরত্ব ও বিস্ময়কর সাহসিকতার অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপিত হইয়াছিল, তাহাতে কোন ব্যাক্তিকে অপৌরুষ ও ভীরুতার দায়ে অভিযুক্ত কয়া এবং প্রকাশ্যভাবে উক্তরুপে ঘোষণা দেওয়া মৃত্যু অপেক্ষাও অনেক কঠিন ব্যাপার ছিল। অতঃপর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে সমাজে মুখ দেখাইবার কোন স্থান আর অবশিষ্ট থাকিত না।
হযরত উমর(রা) সমস্ত সৈনিকদের জন্য বায়তুলমাল হইতে বেতন নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। এই বেতনের কোন নির্দিষ্ট হার ছিলনা। ইসলামী আদর্শ অনুসরণের ক্ষেত্রে শ্রেষ্টত্ত ও প্রাধান্যই ছিল মুজাহিদদের বেতন নির্ধারণের একমাত্র মাপকাঠি। অবশ্য শেষ পর্যায়ে হযরত আলী (রা) এই পার্থক্যও খতম করিয়া দিয়া সকলের জন্য সমান মানের বেতন চালু করিয়াছিলেন।
ইসলামী বাহিনীতে প্রত্যেক দশজন সৈনিকের উপর একজন ‘প্রধান’ নিযুক্ত হইত।আরবী সামরিক পরিভাষায় তাহাকে বলা হইত ‘আরীফ’। এই আরীফদের হস্তেই সকল সৈনিকদের বেতন অর্পণ করা হইত; তাহারা অধীনস্থ সৈনিকদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিত।
সৈন্যবাহিনী সংগঠনের ব্যাপারে খুলাফায়ে রাশেদুনের আমলে যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়। প্রাক-ইসলাম যুগে আরবগণ শত্রুপক্ষকে কখনো সারিবদ্ধভাবে আর কখনো বিচ্ছিন্নভাবে মুকাবিলা করার জন্য অগ্রসর হইত। প্রথমে উভয় পক্ষ হইতে এক-দুইজন বীরপুরুষ সম্মুখ-সমরে লিপ্ত হইত,তাহার পর সাধারণ হামলা পরিচালিত হইত এবং শেষ পর্যন্ত এলোমেলোভাবে আক্রমণ ও অস্ত্র পরিচালনা করা হইত। মুসলমানগণও ইসলামী জিহাদের প্রথম পর্যায়ে এই রীতিরই অনুসরণ করিতেছিলেন। কিন্তু উত্তরকালে তাহারা যখন পারস্য ও রোমানদের সুসংগঠিত সৈন্য বাহিনীর মুখামুখী হইতে আরম্ভ করিলেন, তখন তাঁহারা সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিলেন যে, আধুনিক পদ্ধতিতে এই সংগঠিত সৈন্যবাহিনী ও সমর নীতির মুকাবিলা করিতে হইলে প্রাচীন রীতি অবশ্যই পরিহার করিতে হইবে। অতঃপর তাহারা নূতনভাবে নিজেদের সৈন্যবাহিনী গড়িয়া তোলেন ও সম্পূর্ণ আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করিতে শুরু করেন। যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যবাহিনীকে সুষ্ঠুরূপে সারিবদ্ধ করা হইতে লাগিল, কেহ অগ্রে বা পশ্চাতে পড়িয়া থাকিত না। গোটা সৈন্যবাহিনীকে মোটামুটি পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করা হইত। সকলের অগ্রবর্তী বাহিনীকে বলা হইত ‘মুকদ্দমা’, যুদ্ধের সূচনা করাই হইত ইহার দায়িত্ব। মধ্যবর্তী বাহিনীকে বলা হইত ‘কলব’, মূল সেনাধ্যক্ষ ইহাদের দ্বারাই পরিবেষ্টিত থাকিতেন। ডান পার্শ্বে স্থাপিত বাহিনীকে বলা হইত ‘মায়মানা’ এবং বাম পার্শ্বে অবস্থিত ‘মায়সারা’। আর সকলের পশ্চাতে অবস্থিত বাহিনীর নাম দেওয়া হইত ‘সাকাহ’।
যে সৈন্যবাহিনী এই পাঁচটি উপ-বাহিনীতে বিভক্ত হইত, উহাকে ‘খামীস’ বলা হইত। ইহার প্রত্যেক অংশেরই একজন করিয়া ‘আমীর’ হইতেন এবং তিনি মূল সেনাধ্যক্ষের ফরমান অনুসারে নিজ নিজ বাহিনী পরিচালনা করিতেন।অশ্বারোহী বাহিনীর আমীর হইতেন স্বতন্ত্র। পশ্চাদ্দিক সংরক্ষণের জন্য মুসলিম সৈনিকগন বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করিতেন,যেন শত্রু-সৈন্য কোন সুযোগেই পশ্চাদ্দিক হইতে তাহাদের উপর হামলা করিতে সমর্থ না হয়। নৈশকালীন আক্রমণ হইতে গোটা বাহিনীকে হেফাজত করার জন্য তাঁহারা বিশেষ ব্যবস্থা ও কর্মপন্থা গ্রহণ করিতেন। মুসলমানদের সামরিক গোয়েন্দা বিভাগ ছিল সর্বাধিক সুসংগঠিত ও সুসংবদ্ধভাবে সক্রিয়। সেই কারণে শত্রুদের অধিকাংশ গোপন ইচ্ছা বা পরিকল্পনা তাঁহারা পূর্বাহ্ণেই জানিতে পারিতেন।
রাজস্ব বিভাগ
হযরত উমর (রা)-এর খিলাফত কাল হইতে রাজস্ব আদায়ের জন্য স্বতন্ত্র ও স্থানীয়ভাবে লোক নিয়োগ করা হইত। প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের উপর রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব সাধারণতঃ অর্পণ করা হইত না। আদায়কৃত রাজস্ব খলীফার নির্দেশ অনুসারে সৈনিকদের বেতন-ভাতা ও জনকল্যাণমূলক অন্যান্য সর্বজনীন কাজকর্মে ব্যয় করা হইত। উদ্ধৃত অর্থ কেন্দ্রীয় রাজধানীতে পাঠাইয়া দেওয়া হইত।
খিলাফত আমলে দুই প্রকারের রাজস্ব ধার্য করা হইতঃ(১)স্থায়ী ও (২)অস্থায়ী। স্থায়ী রাজস্বের মধ্যে যাকাত,উশর ও জিজিয়া উল্লেখযোগ্য। পক্ষান্তরে গনিমতের মাল ছিল অস্থায়ী রাজস্ব বা রাষ্ট্রীয় আয়।
খারাজ
সাধারনতঃযুদ্ধ-জয়ের ফলে অধিকৃত দেশের যাবতীয় চাষযোগ্য জমি উহার পূর্বতন মালিকদের নিকটই থাকিতে দেওয়া হইত। অবশ্য উৎপন্ন ফসলের একটি নির্দিষ্ট অংশ রাজস্ব বাবদ আদায় করিয়া লওয়া হইত। ইহাকেই ইসলামী পরিভাষায় বলা হয় ‘খারাজ’। ইহাকে ভোগ্য জমির খাজনা মনে করা যাইতে পারে। কোন কোন ক্ষেত্রে আবার জমির পরিমাণ অনুযায়ী নির্দিষ্ট মুদ্রা কর-বাবদ ধার্য করা হইত।
উশর
যেসব জমির মালিকগণ ইসলাম কবুল করিত অথবা বিজয়ী মুসলমানরা যেসব জমির মালিকদের নিকট হতে জিজিয়া আদায় করিতেন না, সেই জমিকে বলা হয় উশরী জমি এবং উহার ফসলের এক দশমাংশ কিংবা বিশ ভাগের এক ভাগ সরকারী ব্যবস্থাপনায় আদায় কর হইত। মুসলমানগণ বল প্রয়োগ বা যুদ্ধের পরিণতিতে যেসব জমি দখল করিতেন, তাহা ‘উশরী’ জমি নামে অভিহিত হইত এবং তাহা কেবলমাত্র মুসলমানদের মধ্য বণ্টন করিয়া দেওয়া হইত। ফলে তাহা মুসলমানদেরই দখলিভুক্ত হইয়া থাকিত।
হযরত উমর (রা)- এর খিলাফতকালে যখন সিরিয়া ও ইরাক অধিকৃত হয়, তখন তিনি বিজিত জমি সম্পর্কে উপদেষ্টাদের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে,উহার বিলি-ব্যবস্থা কি ভাবে কর হইবে? অধিকাংশ লোকই জমিগুলিকে মুসলমানদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়ার পরামর্শ দিয়াছিলেন।
হযরত উমর (রা)বলিয়াছিলেনঃ ‘তাহা হইলে তো ভবিষত বংশধরদের হক নষ্ট করা হইবে। কেননা, বর্তমানে জমিসমূহ বণ্টন করিয়া দিলে অনাগত মানুষদের জন্য কিছুই অবশিষ্ট থাকিবে না’। উহাতে হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ(রা)বলিলেনঃ জমি ও দাস-দাসী তাহারাই পাইবার অধিকারী, যাহারা নিজেদের বাহুবলে দেশ জয় করিয়াছে; অন্য লোকদের তাহাতে কি অধিকার থাকিতে পারে? ইহার উত্তরে খলীফা উমর ফারুক (রা) বলিলেনঃ ‘একথা ঠিক, কিন্তু মনে রাখিও আমার পর খুববেশী দেশ জয়ের সম্ভবনা থাকিবে না বলিয়া তখন মুসলমানদের পক্ষে অধিক পরিমাণ মাল-দৌলত ও জমি লাভ করা সম্ভব হইবে না। উত্তরকালে বরং অনেক দেশজয় কল্যাণের পরিবর্তে দুর্বহ বোঝার কাজই করিবে বেশী। ইরাক ও সিরিয়ার জমি উহার মালিকদের নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়া ও বিজিত লোকদেরকে ক্রীতদাস বানাইয়া বিজয়ী মুসলামানের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিলে সীমান্তের সংরক্ষণ ব্যবস্থা কিরূপে কার্যকর হইবে? কেননা মুসলামানগণ তো কৃষিকাজে ব্যস্ত হইয়া পড়িবে। এতদ্ব্যতীত ইয়াতীম ও অসহায় বিধবাদের ভরণ-পোষণের কাজও অসমাপ্তিই থাকিয়া যাইবে’।
খলীফা উমর ফারুক(রা)-এর এই ভাষণ শ্রবণ করার পর সকলে একবাক্যে বলিয়া উঠিলেনঃ “আপনার মত বাস্তবিকই সঠিক ও নির্ভুল, তাহাতে সন্দেহ নাই। সীমান্তে ও শহরে যদি সৈন্যবাহিনী নিয়োজিত না থাকে, তাহা হইলে এইসব এলাকা সংরক্ষণ করার কোনই ব্যবস্থা থাকিবে না এবং ইসলামের দুশমনগণ পুনরায় এই শহরগুলির উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া বসিবে”।হযরত উমর বলিলেনঃ এই ব্যাপারটি তো পরিস্কার হইয়া গেল। এখন আমার এমন একটি লোকের প্রয়োজন, যিনি খারাজ নির্ধারণের জন্য সমগ্র ইরাকের জরীপ কার্য সম্পাদনের দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন’। অতঃপর উমরান ইবন হানীফকে এই কাজে নিযুক্ত করা হইল। তিনি অত্যন্ত পরিশ্রম সহকারে এই কাজ সম্পন্ন করিলেন এবং হযরত উমর (রা)- এর শাহাদাত লাভের এক বৎসর পূর্বেই সওয়াদে কুফা হইতে আদায়কৃত খারাজের পরিমাণ এক কোটি মুদ্রা পর্যন্ত পৌঁছিয়াছিল।
সিরিয়া বিজয়ের পরও সৈনিকদের পক্ষ হইতে অধিকৃত জমি সৈনিকদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়ার দাবি উত্থাপিত হয়। কিন্তু তখনও হযরত ফারুকে আজম (রা) উক্তরুপ জওয়াব দিয়া সকলকে নিরস্ত করেন। ফলে ইরাকের ন্যায় সিরিয়ার ভূমি হইতেও বিপুল পরিমাণ খারাজ সরকারী খাজাঞ্জীতে সঞ্চিত হইতে থাকে।
বস্তুতঃ বিজিত এলাকার জমিক্ষেত বিজয়ীদের মধ্যে বণ্টন না করিয়া পুরাতন বাসিন্দাদের দখলে উহা থাকিতে দেওয়া এবং তাহাদিগকে উহার চাষাবাদ করার সুযোগ দিয়া তাহাদের নিকট হইতে খারাজ আদায় করা সম্পর্কে হযরত উমর ফারুক (রা)- এর অভিমত অত্যন্ত দূরদর্শীতার পরিচায়ক ছিল। তখন এইরূপ ফয়সালা গৃহীত না হইলে মুসলিম জাতি তাহার আসল দায়িত্ব ভুলিয়া গিয়া ক্ষেত-খামার লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িত এবং সামরিক দক্ষতা হারাইয়া ফেলিত।দ্বিতীয়তঃসেই এলাকার সংরক্ষণকারী ও অন্যান্য দেশ ও অঞ্চলে যুদ্ধলিপ্ত ইসলামী সৈনিকদের প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহেরও কোন ব্যবস্থা করা সম্ভব হইত না। আর ইহাই হইত সর্বাপেক্ষা মারাত্মক ও অপূরনীয় ক্ষতি। কেননা, এই সুযোগে পারসিক ও রোমক সরদার যা নিজেদের দেশের উপর মুসলিম আধিপত্য স্থাপিত হওয়ায় দেশত্যাগ করিয়া অন্যত্র আশ্রয় লইয়াছিল তাহারা পুনরায় নিজেদের দেশ দখল করিয়া বসিতে পারিত ও মুসলমানদের উপর প্রবলভাবে আক্রমণ চালাইত।
জিযিয়া
ইসলামী খিলাফতে যিম্মিদের(অমুসলিম অনুগত নাগরিকদের) নিকট হইতে তাহাদের জান-মাল ও ইজ্জত-আবরু সংরক্ষণ ও উহার নিরাপত্তার বিনিময়ে যে অর্থ গ্রহণ করা হইত, ইসলামী পরিভাষায় উহাকে ‘জিযিয়া’ বলা হয়। ইহা কেবলমাত্র বয়স্ক ও সুস্থ-সবল পুরুষদের নিকট হইতেই আদায় করা হইত। নারী,শিশু, দরিদ্র ও পঙ্গুদের উপর ইহা ধার্য করা হইত না। হযরত উমর (রা) বহু দরিদ্র যিম্মীর জন্য বায়তুলমাল হইতে বৃত্তি মঞ্জুর করিয়াছিল। ‘জিযিয়া’ ধার্য হইত ব্যক্তির আর্থিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এবং উহার পরিমাণ ১২ দিরহামের কম ও ২৮ দিরহাম অপেক্ষা বেশী হইত না। হযরত উমর (রা) তাহার পরবর্তী খলিফাদিগকে যিম্মীদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন, নম্র আচরণ করা, প্রতিশ্রুতি পালন ও তাহাদের জান-মাল সংরক্ষণের জন্য লড়াই করা এবং তাহাদের উপর সামর্থ্যাপেক্ষা অধিক দায়িত্ব-ভার অর্পণ না করার জন্য বিশেষভাবে উপদেশ দান করিয়াছেন।
যাকাত
খিলাফতের আমলে মুসলমানদের সকল প্রকার সঞ্চিত ধন,গৃহপালিত পশু, নগদ সম্পদ ও জমির ফসলের উপর কুরআন ও সুন্নাহ মুতাবিক যাকাত ধার্য করা হইয়াছিল। এই যাকাত রীতিমত আদায় করা হইত এবং উহার প্রাপক আটটি শ্রেণীর মধ্যে উহা বণ্টন করা হইত।
শুল্ক
মুসলিম ব্যবসায়ীগণ যখন বিদেশে নিজেদের পণ্য রফতানি করিতেন, তখন তাঁহাদের নিকট হইতে সেই দেশ এক দশমাংশ শুল্ক বাবদ আদায় করা হইত।হযরত উমর (রা) যখন ইহা জানিতে পারিলেন, তখন তিনিও ইসলামী রাজ্যে আমদানিকৃত পণ্যের উপর অনুরূপ পরিমাণ শুল্ক ধার্য করার নির্দেশ দান করিলেন। এতদ্ব্যতীত যিম্মী ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে বিশভাগের একভাগ ও মুসলিম ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে সমগ্র সম্পদের চল্লিশভাগের একভাগ আদায় করা হইত। তবে দুইশত দিরহামের কম মূল্যের সম্পদের উপর কিছুই ধার্য করা হইত না।
মুদ্রা
আরবদেশের ইসলামের পূর্বে স্বর্ণ ও রৌপ্যের ইরানী ও রোমীয় মুদ্রা প্রচলিত ছিল। নবী করীম(স) ও হযরত আবূ বকরল (রা)-এর খিলাফত কালেও এই মুদ্রাই চালু ছিল। ইরান বিজয়ের পর হযরত উমর(রা) দিরহামের ওজন করিবার ইচ্ছা ব্যক্ত করিয়াছিলেন। কেননা ইরানী মুদ্রায় ওজন বিভিন্ন প্রকারের হইত। মোট কথা খিলাফতে রাশেদার আমলে আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার পূর্ণাঙ্গ রূপ বর্তমান ও কার্যকর ছিল এবং উহা কোন দিক দিয়াই পশ্চাদবর্তী ছিল না।
হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)
ইসলামী গণ-রাষ্ট্রের প্রথম খলীফা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক(রা)। ইসলামের ইতিহাসে রাসূলে করীম হযরত মুহাম্মাদ(স)-এর পরেই হযরত আবূ বকর (রা)-এর স্থান। ইসলামী ঐতিহ্যের দিক দিয়াও রাসূলের পর তিনিই সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য ব্যাক্তি। নবী করীম(স) তাঁহার তেইশ বৎসরকালীন সাধনার মাধ্যমে যেখানে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ জীবনাদর্শ উপস্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে আরবের কঠিন জাহিলিয়াতের প্রাসাদ চুরমার করিয়া উহার ধ্বংসস্তূপের উপর ইসলামের উজ্জ্বল আদর্শ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন,সেখানে হযরতের ইন্তেকালের অব্যবহিত পরই জাহিলিয়াতের প্রতিবিপ্লবী শক্তির উত্তোলিত মস্তক চূর্ণ করিয়া দিয়া ইসলামী রাষ্ট্রের অস্তিত্ব রক্ষা করিয়াছেন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)। এই জন্য নবী জীবনের আলোচনা-পর্যালোচনার সঙ্গে প্রথম খলীফা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক(রা)-এর জীবনচরিত অধিকতর গুরুত্ব সহকারে আলোচনা করা আবশ্যক। বর্তমান প্রবন্ধে আমার হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর পূর্ণাঙ্গ জীবনী আলোচনা করিব না। তাঁহার গুন-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা পেশ করাই এই প্রবন্ধের একমাত্র উদ্দেশ্য।
কালের গতি-স্রোতে অতীত,বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ এমনভাবে ওতপ্রোতভাবে জড়িত যে, ইহার কোন একটি পর্যায়কে অপরটি হইতে কিছু মাত্র বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখা যায় না। যে কোন জাতির ভবিষ্যত পথ-নির্দেশের জন্য উহার অতীতকে গভীর ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পর্যালোচনা করাই সর্বাধিক উত্তম পন্থা। জাতীয় জীবনে যে ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয়, তাহা হইতে জাতিকে উদ্ধার করার জন্যও তাহার উজ্জ্বল অতীতকেই লোকদের সম্মুখে তুলিয়া ধরা আবশ্যক। রুগ্ন ব্যক্তির রোগ নির্ণয় ও নির্ধারণ এবং উহার চিকিৎসা বিধানের জন্য যেমন রোগপূর্বকালীন অবস্থা আদ্যপান্ত পর্যালোচনা করা আবশ্যক, অনুরুপভাবে জাতীয় রোগ নির্ধারণ ও চিকিৎসা বিধানের জন্য অতীত ইতিহাস আলোচনা এবং ঐতিহাসিক ব্যক্তিদের জীবন পর্যালোচনার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। বর্তমান সময়ে বিশ্বের মুসলিম জাতি অধঃপতনের চরম সীমায় উপনীত। এই মুহূর্তে হযরত আবূ বকর (রা)-এর জীবনাদর্শ নিঃসন্দেহে মুসলিম জাতির জীবন-পথের দিশারী হিসেবেই মর্যাদা পাইবে।
হযরত আবূ বকর সিদ্দীক(রা) পুরুষদের মধ্য সর্বপ্রথম হযরত মুহাম্মাদ (স)-কে সত্যিকার নবী বলিয়া বিশ্বাস স্থাপন করেন। তাঁহার এই ঈমানই উত্তরকালে তাঁহাকে ‘সিদ্দীক’ বা ‘সত্য-স্বীকারী’ উপাধিতে ভূষিত হইবার গৌরব দিয়াছে। নবুয়্যাতের দীর্ঘ তেইশ বৎসরে তিনি দ্বীন-ইসলামকে কায়েম করার প্রচেষ্টায় জান-মাল ও ইজ্জত পর্যন্ত কুরবান করিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হন নাই; বরং এই ক্ষেত্রে তিনি অপরাপর সাহাবী এবং সমস্ত মুসলমানদের অপেক্ষা অধিক অগ্রসর ছিলেন। ইস্লাম্র কবুল করার পর হইতে রাসূলে করীম (স)-এর ইন্তেকাল পর্যন্ত দীর্ঘকাল তিনি হযরতের সাহায্য-সহযোগিতা,দ্বীন-ইসলামের প্রচার ও কাফিরদের অত্যাচার-নিষ্পেষণ হইতে মুসলমানদের রক্ষা করার ব্যাপারে প্রতিনিয়ত ব্যস্ত-সমস্ত থাকতেন। রাসূলের প্রতিটি নির্দেশকে তিনি নিজের সমস্ত কাজের উপর প্রাধান্য দান করিতেন। রাসূলের জন্য তিনি নিজ জীবনেরও কোন পরোয়া করেন নাই। কাফিরদের সহিত প্রতিটি প্রত্যক্ষ সংগ্রামে তিনি রাসূলের কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া লড়াই করিয়াছেন। ঈমানের অভূতপূর্ব দৃঢ়তা ও ইস্পাত-তুল্য অনমনীয়তার পাশাপাশি তাঁহার উন্নত চরিত্র বিশ্ব-মুসলিমের জন্য এক অতুলনীয় আদর্শ। এই কারণেই তিনি ছিলেন অতীব জনপ্রিয় ব্যক্তি;তাঁহার প্রতি গোটা মুসলমানের ভালবাসা ছিল অপূর্ব।
হযরত আবূ বকর (রা)- দ্বীনী মর্যাদা এবং তাঁহার প্রতি জনগণের অসীম ভক্তি-শ্রদ্ধার কারণেই, রাসূল করীম(স) যখন রোগশয্যায় শায়িত, তখন খোদ রাসূলই তাঁহাকে নামাযে ইমামতী করার জন্য নির্দেশ দান করেন। ইহা ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ একটি ঘটনা। অতঃপর রাসূলের ইন্তেকালের পর তাঁহাকেই ইসলামী রাষ্ট্রের প্রথম খলীফা নির্বাচিত করা হয়। মুসলমানদের সাধারণ পরিষদে বিস্তারিত আলাপ-আলোচনার পর সর্বসম্মতিক্রমে তিনিই খলীফা নির্বাচিত হন। এই সময় খলীফা নির্বাচিত হইয়াই তিনি যে মূল্যবান ভাষণ দান করেন, বিশ্ব-মুসলিমের নিকট তাহা যেমন এক ঐতিহাসিক বিষয়, ইসলামী রাষ্ট্র-দর্শনের ক্ষেত্রেও উহা চিরন্তন পথ-নির্দেশক। তাঁহার এই ভাষণের পূর্ণাঙ্গ রূপ এখানে উদ্ধৃত করা যাইতেছে। তিনি সমবেত জনতাকে সম্বোধন করিয়া গুরুগম্ভীর কণ্ঠে বলেনঃ
০হে মানুষ!রাষ্ট্রনেতা হওয়ার বাসনা আমার মনে কোন দিনই জাগ্রত হয় নাই, আমি নিজে কখনও এই পদের আকাঙ্ক্ষী ছিলাম না। ইহা লাভ করার জন্য আমি নিজে আল্লাহ্র নিকট গোপনে কিংবা প্রকাশ্যে কখনও প্রার্থনাও করি নাই।
০আমি এই দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছি কেবলমাত্র এইজন্য যে, দেশে যেন কোন প্রকার বিপর্যয় সৃষ্টি হইতে না পারে।
০সরকারী ক্ষমতায় আমার মনে বিন্দুমাত্র শান্তি ও স্বস্তি নাই।
০আমার উপর এত বড় দায়িত্ব চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, আল্লাহ্র সাহায্য না পাইলে আমি তাহা সুসম্পন্ন করিতে পারিব না।
০আমাকে তোমাদের পরিচালক নিযুক্ত করা হইয়াছে,অথচ আমি তোমাদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি নহি।
০আমি যদি সোজা ও সঠিক পথে চলি, তবে তোমরা আমার সাহায্য ও সহযোগিতা করিও। আর আমি যদি ন্যায়পথ পরিত্যাগ করি, তবে তোমরা আমাকে সঠিক পথে পরিচালিত করিও।
০সত্যতা হইতেছে আমানত আর মিথ্যা বিশ্বাসঘাতকতা।
০তোমাদের মধ্যে প্রভাবহীন ব্যক্তিই আমার দৃষ্টিতে হইবে প্রভাবশালী; তাহার সকল প্রকার অধিকার আমি আদায় করিয়া দিব।
০আর যে ব্যক্তি খুবই প্রভাবশালী, আমার নিকট তাহার কোন প্রভাবই থাকিবে না, তাহার উপর দুর্বল ব্যক্তির কোন ‘হক’ থাকিলে তাহা পুরাপুরি আদায় না করিয়া আমি ক্ষান্ত হইব না।
০যে জাতির মধ্যে অন্যায়, পাপ ও নির্লজ্জতা প্রসার লাভ করে, সে জাতির উপর আল্লাহ্র আযাব নাযিল হয়।
০আমি যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ এবং তাঁহার রাসূলের আনুগত্য করিব ততক্ষণ তোমরাও আমার আনুগত্য করিবে।
০আর আমি যদি আল্লাহ্ এবং তাঁহার রাসূলের নাফরমানী করি, তবে আমার আনুগত্য করা তোমাদের কর্তব্য হইবে না।
হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) তাঁহার সংক্ষিপ্ত খিলাফতকালে ইসলামের শ্রেষ্টত্ত বিধানের জন্য যে দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা চালাইয়াছেন, বিশ্ব-মুসলিমের ইতিহাসে তাহার কোন তুলনা নাই। প্রকৃতপক্ষে তাঁহারাই খিলাফতকালে ইসলামী রাষ্ট্র-ব্যবস্থার বুনিয়াদ সুদৃঢ় হয় এবং উহা বিশ্বের বিশাল অংশে সম্প্রসারিত হয়। এই বিরাট রাষ্ট্র এশিয়ার ভারতবর্ষ ও চীন পর্যন্ত এবং আফ্রিকার মিশর,তিউনিসিয়া ও মরক্কো পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। মোটকথা, এই রাষ্ট্রই মানবীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির উৎকর্ষ সাধনের জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করিয়াছে-যাহার প্রত্যক্ষ প্রভাব দুনিয়ার শেষ মুহূর্তে পর্যন্ত অব্যাহত থাকিবে।
হযরত আবূ বকর সিদ্দীক(রা) ছিলেন রাসূলে করীম(স)-এর চিরন্তন সহচর, প্রাণ উৎসর্গীকৃত বন্ধু এবং অকৃত্রিম ও একনিষ্ঠ অনুগত। তাঁহার অন্তর ছিল অত্যন্ত দরদী। অতুলনীয় গুণ-বৈশিষ্ট্যে তিনি ছিলেন বিভূষিত।
প্রথম খলীফা নির্বাচিত হওয়ার পর ইসলামের উপর মুর্তাদ তথা ইসলাম ত্যাগকারীগণের প্রতিবিপ্লবী কর্মকাণ্ডের চরম আঘাত আসে। বস্তুতঃএই সময় ইসলামী রাষ্ট্রের সম্মুখে এক নাজুক পরিস্থিতি দেখা দেয়। কিন্তু একমাত্র আবূ বকর (রা)-এর অতুলনীয় ব্যক্তিত্বই ইসলামী রাষ্ট্রের এই অংকুরকে প্রতিবিপ্লবী কর্মকাণ্ডের আঘাত হইতে রক্ষা করিয়াছে এবং মুসলিম জনগণকে ধ্বংস ও বিপর্যয়ের কবল হইতে বাঁচাইয়াছে। তিনি পারস্য ও রোমক রাষ্ট্রসমূহের বিরুদ্ধে সৈন্য পরিচালনা করিয়া ইসলামের সমস্ত শত্রুতা অংকুরেই খতম করেন এবং ইহার পর যে রাষ্ট্র গড়িয়া উঠে,বিশ্ব-জাতিসমূহের মানসপট হইতে উহার প্রভাব আজিও মুছিয়া যায় নাই এবং কোন দিনই তাহা মুছিয়া যাইতে পারে না।
হযরত আবূ বকর (রা)-এর খিলাফত যুগের ইতিহাস বড়ই বিস্ময়-উদ্দীপক। এই ইতিহাস হইতেই তাহার বিরাট ব্যক্তিত্তের আশ্চর্যজনক দিকগুলি আমাদের সম্মুখে উজ্জ্বল হইয়া উঠে। এই মহান সত্যসেনানী গরীব ও মিসকীনের সাহায্য কাজে প্রতিনিয়ত ব্যস্ত থাকিতেন। তাঁহার দরিদ্র-সেবার নমুনা দেখিলে প্রতীয়মান হয় যে, তাঁহার ন্যায় গরীব-দরদী ভূ-পৃষ্ঠে দ্বিতীয় কেহ নাই। অপরদিকে ইসলাম প্রচার ও ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে তাঁহার বীরত্বসূচক পদক্ষেপও জীর্ণ জাতির বুকে নব জীবনের স্পন্দন জাগায়। হযরত আবূ বকর (রা)-এর সাহস, হিম্মত, দৃঢ়তা ও বিরত্তের সম্মুখে তৎকালীন দুনিয়ার সম্মিলিত শক্তিও ছিল তৃণখণ্ডের ন্যায় হীন ও নগণ্য। সংকল্প ও দৃঢ়তার এই প্রতীক প্রবর কুণ্ঠা, সংকোচ ও ইতস্ততার সহিত কিছুমাত্র পরিচিত ছিলেন না। লোকদের অন্তর্নিহিত প্রতিভা, শক্তি ও যোগ্যতা সম্পর্কে নির্ভুল ধারণা পোষণ করা এবং যোগ্যতা ও প্রতিভা অনুসারে বিভিন্ন মানুষকে বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত করা ও তদানুযায়ী তাহাদের নিকট হইতে কাজ আদায় করার ব্যাপারে তাঁহার যোগ্যতা ও দূরদৃষ্টি ছিল নিঃসন্দেহে অতুলনীয়।
রাসূলে করীম (স)- এর জিবদ্দশায় হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) একনিষ্ঠ রাসূল-প্রেমিক হিসেবেই জীবন যাপন করিয়াছেন। দুর্ধর্ষ কুরাইশগণ যখন রাসূলে করীম(স)-এর উপর নানাবিধ অমানুষিক অত্যাচার-উৎপীড়ন করিত, তখন হযরত আবূ বকর (রা)ই তাহাদের মুকাবিলায় বুক পাতিয়া দিতেন। রাসূলুল্লাহর ইসলামী দাওয়াত সর্বপ্রথম তিনিই কবুল করিয়াছেন এবং হিজরাতের কঠিন ও নাজুক অবস্থায় ‘সওর’ পর্বত-গুহা হইতে মদীনা পর্যন্ত মরু ও পর্বত-সংকুল বন্ধুর পথে পূর্ণ প্রাণোৎসর্গ সহকারে রাসূলুল্লাহর বিশ্বস্ত সহচর হিসেবে রহিয়াছেন। মদিনায় রাসূলে করীম(স)-কে ইয়াহুদীদের ষড়যন্ত্র ও মুনাফিকদের কুটিলতার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল এবং মক্কার কুরাইশ ও মদীনার ইয়াহুদীদের উপর্যুপরি শত্রুতামূলক তৎপরতার ফলে সমস্ত আরব দেশ রাসূলের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিয়াছিল। এই জটিল সময়ে হযরত আবূ বকর (রা) ই নবী করীম(স)-এর বিশেষ সহচর ও পরামর্শদাতা হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করিয়াছেন।বস্তুত ইসলামের শ্রেষ্টত্ত প্রতিষ্ঠার জন্য আবূ বকর (রা) যে ভূমিকা অবলম্বন করিয়াছেন এবং রাসূলের জীবদ্দশায় তিনি এই প্রসঙ্গে যে বিরাট খেদমত আঞ্জাম দিয়াছেন, সমষ্টিগতভাবে তাহা কেবল স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া রাখার বস্তুই নহে, উহার প্রতিটি বিষয়ে এককভাবে তাঁহার জীবনকে চিরদিনের তরে জীবন্ত করিয়া রাখার জন্য যথেষ্ট। প্রকৃতপক্ষে হযরত আবূ বকর (রা)-এর শ্রেষ্টত্ত ও মর্যাদা ভাষায় বর্ণনা করা এক সুকঠিন ব্যাপার। কেননা ইসলামের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি যে ত্যাগ ও কুরবানী দান করিয়াছেন, তাহা মূলতঃই হৃদয় ও ঈমানের ব্যাপার। তাঁহার হৃদয়ে ইসলাম ও রাসূলে করীম (স)-এর জন্য যে গভীর ভালবাসা বিদ্যমান ছিল, তাহা একমাত্র আল্লাহ্ তা’আলাই ভাল জানেন। রাসূলের ইন্তেকালের পর হযরত আবূ বকর (রা)-এর খিলাফত আমলে যে সব ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে এবং তাহাতে তিনি যে নীতি ও পদক্ষেপ গ্রহন করিয়াছেন, তাহা হইতেই প্রথম খলীফার সুতীক্ষ্ণ বিচক্ষণতা,দূরদৃষ্টি এবং গভীর ও সূক্ষ্ম জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার খলীফা নির্বাচিত হওয়ার অব্যবহিত পরই মুর্তাদগণ মাথাচাড়া দিয়ে উঠিলে তিনি অত্যন্ত দৃঢ়তাসহকারে তাহাদের মুকাবিলা করেন এবং কঠিন হস্তে বিদ্রোহীদের মস্তক চূর্ণ করিয়া দেন। অতঃপর তিনি পারস্য ও রোম সাম্রাজ্যের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। এই দুইটি রাষ্ট্রের ব্যাপারে তিনি যে সাম্যের অস্ত্র প্রয়োগ করিয়াছিলেন তার কবল হইতে আত্তরক্ষা করার মত কোন অস্ত্রই উহাদের নিকট ছিল না। পারস্য ও রোমক সাম্রাজ্যের জনগন ব্যক্তিগত তথা রাজতন্ত্রের নিষ্ঠুর পেষণে নিষ্পেষিত হইতেছিল। উভয় সাম্রাজ্যের প্রজাসাধারণ বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। বংশীয়-গোত্রীয় বৈষম্য ও পার্থক্যের অভিশাপ উভয় জাতির উপরই জগদ্দল পাথরের ন্যায় চাপিয়াছিল। শাসকগণ জনসাধারণকে নীচ বলিয়া মনে করিত এবং তাহাদিগকে সকল প্রকার মান-মর্যাদা ও অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখাই নিজেদের কর্তব্য বলিয়া মনে করিত। ঠিক এই সময়ই হযরত আবূ বকর (রা) ইসলামের বিচার,ইনসাফ ও সাম্যের পতাকা উড্ডীন করেন। তিনি পারস্য ও রোম আক্রমণকারী সেনাধ্যক্ষগণকে সুবিচার, ইনাসাফ ও সাম্যের মানদণ্ড এক মুহূর্তের তরেও হস্তচ্যুত না করার জন্য বিশেষ হেদায়েত প্রদান করেন এবং বিজিত দেশের সমস্ত জনগণের প্রতি জাতি,ধর্ম, বংশ নির্বিশেষে সাম্যের আচরণ অবলম্বন করার সুস্পষ্ট নির্দেশ দেন। ফলে যুগান্তকালব্যাপি জুলুম-পীড়ন, নির্যাতন-নিষ্পেষণ ও অসাম্য-অবিচারে জর্জরিত জনতা ইসলামের উদার সাম্য ও সুবিচার নীতির আলোকচ্ছাটায় মুগ্ধ হইয়া বাঁধভাঙ্গা বন্যার ন্যায় উচ্ছসিত হইয়া উঠে এবং উক্ত রাষ্ট্রদ্বয়ের বিরাট সামরিক শক্তি ও দুর্জয় সশস্ত্র বাহিনী বর্তমান থাকা সত্ত্বেও মুসলমানদের মুষ্টিমেয় অস্ত্র-শক্তিহীন বীর মুজাহিদীনের নিকট পরাজয় বরণ করিতে বাধ্য হয়।
রাসূলে করীম (স)-এর জীবনকাল ও খিলাফতের দ্বিতীয় পর্যায় তথা হযরত উমর (রা)-এর খিলাফত কালের মধ্যে হযরত আবূ বকর (রা)-এর খিলাফতের একটি বিরাট স্বাতন্ত্র্য ও বিশিষ্ট মর্যাদা বিদ্যমান। রাসূলের যুগ মূলত পথ-নির্দেশ ও সংশোধন সংস্কারের পর্যায়। শরীয়াতের পবিত্র বিধানসমূহ তখন নাজিল হয়। আল্লাহ্র তরফ হইতে মানবতার চিরন্তন হেদায়েতের জন্য রাসূলের মারফত ক্রমাগতভাবে আইন-কানুন নাজিল হইতেছিল। পক্ষান্তরে হযরত উমর ফারুক (রা)-এর যুগ হইতেছে সাংগঠনিক পর্যায়। তখন নব প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপনা ও যাবতীয় কার্য সম্পাদনের জন্য নিয়ম-কানুন রচিত হইতেছিল; খিলাফতের শাসন-কার্যে শৃঙ্খলা বিধানের জন্য বিভিন্ন বিভাগ গঠন করা হইতেছিল। প্রথম খলীফা হযরত আবূ বকর (রা)-এর খিলাফতকালে উল্লেখিত দুই পর্যায়ের মধ্যবর্তী হইলেও এই সময় উদ্ভুত অসাধারণ ও অস্বাভাবিক পরিস্থিতির দরুণ তাহা এক স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য সমুজ্জল।
হযরত আবূ বকর (রা)-এর খিলাফত কালে যে সব দুর্যোগ ও বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়, তাহাতে গোটা ইসলামই এক কঠিন বিপদের সম্মুখীন হইয়া পড়ে। নবী করীম (স) এর তেইশ বৎসরকালীন সাধনা ও সংগ্রামের ফলে গঠিত ঐক্যবদ্ধ জাতি এক মারাত্মক বিশৃঙ্খলার আঘাতে ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া যাইবার উপক্রম হয়। মূলতঃ রাসূলের জীবনকালে শেষ ভাগেই রাষ্ট্রীয় উচ্ছৃঙ্খলতার সূচনা হয়। মুসাইলামা বিন হাবীব নামক জনৈক ভণ্ড ইয়ামামা হইতে নবী হওয়ার দাবি করিয়া দূত মারফত অর্ধেক আরব তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়ার পয়গাম প্রেরণ করে। অতঃপর আসওয়াদ আনাসী নামক অপর এক ভণ্ডও যাদুখেলা দেখাইয়া ইয়ামনবাসীদিগকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করিতে চেষ্টা করে। এমনকি শক্তি সঞ্চয়ের পর সে ইয়ামনের দক্ষিণ অংশ হইতে রাসূলে করীম (স)-এর নিযুক্ত কর্মচারীদের বিতাড়িত করিয়া উহা নিজের শাসনাধীন করিয়া লয়। এই সময় রাসূলে করীম (স) ইয়ামনে সৈন্য প্রেরণ করিয়া তাহার মস্তক চূর্ণ করার ব্যবস্থা করিতে বাধ্য হন। বস্তুতঃআরবের জনগণ যদিও তওহীদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়া মূর্তিপূজা পরিত্যাগ করিয়াছিল; কিন্তু ইসলামের ধর্মীয় ঐক্য ও রাজনৈতিক শাসন-সংস্থার অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক সম্বন্ধে তাহাদের অনেকেই সম্পূর্ণ অবহিত ছিল না। আরববাসীগণ এমনিতেই ছিল জন্মগতভাবে স্বাধীনতাপ্রিয়; কোন প্রকার সুসংগঠিত রাষ্ট্র-সরকারের অধীনতা স্বীকার করা ও প্রাণ-মন দিয়া উহার আনুগত্য করিয়া যাওয়া তাহাদের ধাতে সহিত না। এই জন্য রাসূলের ইন্তেকালের পর মুহূর্তেই আরবের বিভিন্ন গোত্র মদীনার সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিতে শুরু করে। বিদ্রোহের আগুন তীব্র গতিতে আরবের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়ে। মুর্তাদদের পাশাপাশি অনেকে আবার বায়তুল মালে যাকাত প্রদান করিতে অস্বীকৃত জ্ঞাপন করে। মদীনায় এই সংবাদ পৌঁছিলে লোকদের মধ্যে সাংঘাতিক দুশ্চিন্তা ও অস্থিরতা দেখা দেয়। এই নাজুক পরিস্থিতিতে কি করা উচিত, তাহা তাঁহারা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। কোন কোন সাহাবী-এমনকি হযরত উমর ফারুক (রা)ও-এই মত পোষণ করিতেন যে, যাকাত অস্বীকারকারী লোকদের বিরুদ্ধে এই কঠিন মুহূর্তে কোন সশস্ত্র পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত হইবে না, বরং তাহারা যতক্ষণ পর্যন্ত কালেমায়ে তাইয়েবা ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ পড়িবে ততক্ষন তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা না করাই সমীচীন। তাঁহারা মনে করিতেন যে, বিদ্রোহীদের সঙ্গে সঙ্গে যাকাত অস্বীকারকারীদেরও দমন করার চেষ্টা করিলে যুদ্ধক্ষেত্র অধিকতর বিশাল ও ব্যাপক হইয়া পড়িবে, যাহার পরিণাম ভাল হইবে বলিয়া মনে করা যায় না। কিন্তু বীর খলীফা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)সকল প্রকার বিপদ-শঙ্কা উপেক্ষা করিয়া মুর্তাদ বিদ্রোহীদের ন্যায় যাকাত বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধেও প্রকাশ্য যুদ্ধ ঘোষণা করার সংকল্প প্রকাশ করিলেন এবং এই পদক্ষেপ হইতে তাঁহাকে কোন শক্তিই বিরত রাখিতে পারিল না।
ইসলামের ইতিহাসে মুর্তাদদের বিরুদ্ধে পরিচালিত এই যুদ্ধের গুরুত্ব খুবই অপরিসীম। বস্তুতঃএই যুদ্ধ ইসলাম ও ইসলামী রাষ্ট্রকে চির ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছে বলিলেও কিছু মাত্র অত্যুক্তি হইবে না। কেননা, একথা সুস্পষ্ট যে, মদীনার অধিকাংশ লোকের রায় অনুযায়ী হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) যদি মুর্তাদদের বিরুদ্ধে এই জিহাদ না করিতেন,তাহা হইলে ফিতনা-ফ্যাসাদ কিছুমাত্র প্রশমিত হইত না।আর এই যুদ্ধে ইসলামী ফৌজ যদি জয়যুক্ত না হইত, তাহা হইলে পরিস্থিতির অবর্ণনীয় রূপে অবনতি ঘটিত এবং উহার ফলে ইসলাম ও মুসলমান উভয়ই একেবারে ধ্বংসের সম্মুখীন হইয়া পড়িত।
এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, হযরত আবূ বকর (রা) মুর্তাদদের বিরুদ্ধে শক্তিশালী প্রতিরোধ গড়িয়া তুলিয়া অপূর্ব বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে ইহার দ্বারা তিনি বিশ্ব-ইতিহাসেরই দিক পরিবর্তন করিয়াছেন এবং নূতনভাবে মানবীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন।
মুর্তাদ বিরোধী এই জিহাদে হযরত আবূ বকর (রা) জয়ী না হইলে পারস্য ও রোমক সাম্রাজ্যদ্বয়ের মুকাবিলায় মুসলমানদের সাফল্য লাভ তো দূরের কথা, ইরাক ও সিরিয়ার দিকে মুসলমানদের অগ্রসর হওয়া পর্যন্ত সম্ভব হইত না। তখন এই বিরাট ইসলাম-বিরোধী রাষ্ট্রদ্বয়ের ধ্বংসস্তূপের উপর খৃস্টানদের সভ্যতা-সংস্কৃতির পরিবর্তে ইসলামী তাহজীব-তামাদ্দুনের প্রতিষ্ঠা কোনক্রমেই সম্ভব হইত না।
এই বিরাট জিহাদ সংগঠিত না হইলে সম্ভবতঃহযরত উমর ফারুক (রা) কুরআন মজীদকে গ্রন্থাকারে সন্নিবেশিত করার জন্য হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-কে কোন পরামর্শ দেওয়ারও প্রয়োজন বোধ করিতেন না।
পরন্তু মুর্তাদদের এই বিদ্রোহকে অংকুরেই ধ্বংস করা সম্ভব না হইলে হযরত আবূ বকর (রা) মদীনায় কোন প্রকার মজবুত রাষ্ট্র-সরকারই পরিচালনা করিতে পারিতেন না এবং তাহাঁরই পরিচালিত ইসলামী রাষ্ট্রের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর এক গগনচুম্মি প্রাসাদ তৈয়ার করা হযরত উমর (রা)-এর পক্ষে কখনই সম্ভব হইত না।
বস্তুতঃই এ বিরাট ও বিপ্লবাত্মক ঘটনাবলী মাত্র সাতাইশ মাসের এক সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে সংঘটিত হইয়াছিল। এই স্বল্পকালীন খিলাফতকে এর শ্রেণীর লোক বিশেষ গুরুত্ব দিতে চাহে না; বরং তাহারা খুলাফায়ে রাশেদুন, এমন কি ইসলামী রাষ্ট্র বলিতে দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর ফারুক (রা)-এর খিলাফতকেই বুঝিয়া থাকে এবং জনসমক্ষে উহাকেই পেশ করে। তাহারা মনে করে যে, হযরত আবূ বকর (রা) এই সংকীর্ণ সময়ের মধ্যে খুব বিরাট কোন বিপ্লবাত্মক কাজ সম্পন্ন করিতে পারেন নাই এবং তাহার সংক্ষিপ্ত কর্মকাল এইরূপ কোন কাজের জন্য যথেষ্টও নয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা মোটেই সত্য নহে। বিশ্ব-ইতিহাসের যে সব বিপ্লব মানবতার সম্মুখে উত্তরোত্তর উন্নতির দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে, উহার অধিকাংশই অতি অল্প সময়ের মধ্যে সম্পন্ন হইয়াছে। ইতিহাসে ইহার দৃষ্টান্তের কোন অভাব নাই। বিশ্ব-ইতিহাসে যে ইসলামী রাষ্ট্র-বিপ্লবের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার প্রথম ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন হযরত রাসূলে করীম (স)। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) উহাকে প্রতি-বিপ্লবী আক্রমণের আঘাত হইতে রক্ষা করিয়াছেন এবং হযরত উমর (রা) উহাকে উন্নতির উচ্চতম পর্যায়ে উন্নীত করিয়াছেন। কাজেই উমর ফারুক (রা)-এর উন্নত খিলাফত-রাষ্ট্রকে যথাযথরূপে অনুধাবন করিতে হইলে তাঁহার পূর্ববর্তী এবং নবী করীম (স)-এর পরবর্তী হযরত আবূ বকর (রা)-এর খিলাফতকাল বিস্তারিতরুপে পর্যালোচনা করা একান্তই আবশ্যক। আমরা এই দিকে পাঠকবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করিব।
হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর বৈশিষ্ট্য
বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর ইসলামী দাওয়াত ও আন্দোলনের ফলে যে ইসলামী সমাজ গঠিত হইয়াছিল, হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর পরে উক্ত সমাজের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যাক্তি ছিলেন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)। তাঁহার এই শ্রেষ্টত্ত কেবল বিশ্বনবীর জীবদ্দশায়ই সমগ্র মুসলিম সমাজের নিকট সর্ববাদিসম্মত ছিল না, তাঁহার অন্তর্ধানের পরেও গোটা মুসলিম দুনিয়ায় তিনিই ছিলেন অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠ পুরুষ। বস্তুতঃ এই বিষয়ে অতীত যুগে ইসলামী সমাজের কোন কেন্দ্রেই এবং কখনই এক বিন্দু মতবৈষম্য পরিলক্ষিত হয় নাই। এই ব্যাপারে মত বৈষম্যের কোন অবকাশও ছিল না।
কিন্তু এতৎসত্ত্বেও একথা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই যে, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর এই অবিসংবাদিত শ্রেষ্টত্তের মূলীভূত কারণ এবং তাঁহার বিশেষ গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে খুব কম লোকই অবহিত রহিয়াছেন। নবী করীম (স)-এর জীবদ্দশায় সমস্ত মুলসমানের দৃষ্টি তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হওয়ার প্রকৃত কারণ কি, তাহা মুসলিম মানসের এক অত্যন্ত জরুরী সওয়াল। অথচ একথা সর্বজনজ্ঞাত যে, ইসলামের পূর্বে আরব দেশে শ্রেষ্টত্তের মানদণ্ড হিসাবে যে কয়টি জিনিস সাধারণভাবে স্বীকৃত ছিল, তন্মধ্যে কোন একটি দিক দিয়াই হযরত আবূ বকর (রা)-এর একবিন্দু বিশেষত্ব ছিল না। তিনি কুরাইশের অভিজাত ও সমধিক মর্যাদাসম্পন্ন ‘তাইম’ গোত্রে জন্মগ্রহন করিয়াছিলেন। কিন্তু জাহিলিয়াতের যুগে সমগ্র আরব সমাজের কুরাইশ বংশের অপরাপর শাখা-প্রশাখা যতদূর সম্মান মর্যাদা লাভ করিয়াছিল, হযরত আবূ বকর (রা)-এর গোত্রটিও অনুরূপ মর্যাদার অধিকারী হইয়াছিল;উপরন্তু সুবিজ্ঞ ব্যবসায়ী হিসাবেও তাঁহার যথেষ্ট আর্থিক স্বচ্ছলতা ছিল; কিন্তু কুরাইশ বংশে তাঁহার অপেক্ষা অধিকতর ধনবান ব্যক্তি তখনো জীবিত ছিল। তাঁহার বংশ ও গোত্রের লোকদের আস্থা ও শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন তিনি। কুরাইশের জাহেলী সমাজ-ব্যবস্থায় হযরত আবূ বকর (রা) এবং তাঁহার বংশ ও গোত্রের লোক অন্যান্য লোকদের সমান শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্য কখনই লাভ করিতে পারে নাই। ইসলাম-পূর্ব যুগে বাগ্মিতা,কবিত্ব,গণকতা,নেতৃত্বের কাড়াকাড়ি প্রভৃতি দিক দিয়া হযরত আবূ বকর (রা) বিশেষ অগ্রসর ছিলেন না বলিয়া তিনি তদানীন্তন সমাজের অন্যান্য লোকদের সমপরিমাণ ইজ্জত লাভ করিতে পারেন নাই; কিন্তু তৎসত্ত্বেও কোন সব গুন-বৈশিষ্ট্য ও জনহিতকর কাজের দরুণ মানবেতিহাসের সর্বাপেক্ষা উত্তম ও পবিত্র সমাজ হযরত আবূ বকর (রা)-কে নিজেদের নেতা ও প্রথম খলিফারুপে বরণ করিয়া লইয়াছিল এবং দ্বীন ও দুনিয়ার সমগ্র ব্যাপারে তাঁহার উপর অকুণ্ঠ আস্থা স্থাপন করিয়াছিল? সাধারণভাবে ইতিহাসের প্রতিটি ছাত্র-প্রতিটি মুসলিমের পক্ষেই এই প্রশ্নটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু বর্তমানে যাঁহারা মুসলমান এবং আধুনিক বিশ্ববাসীকে ইসলামী সমাজের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অবহিত করিতে ইচ্ছুক, যাহারা নেতৃত্বের আদর্শ চরিত্র সম্পর্কে মুসলিম জনগণকে শিক্ষিত ও সজাগ করিয়া তুলিতে সচেষ্ট,তাহাদের নিকট এই প্রশ্নের গুরুত্ব অপরিসীম। বস্তুতঃইসলাম সমাজ ও ব্যক্তি গঠনের যে সর্বাঙ্গ সুন্দর আদর্শ ও মানদণ্ড উপস্থাপন করিয়াছে, তাহাই একদা কার্যকর ও বাস্তবায়িত হওয়ার ফলে হযরত আবূ বকর (রা) ও হযরত উমর (রা) প্রমুখের ন্যায় মহান নেতা লাভ করা মুসলমানদের ভাগ্যে সম্ভব হইয়াছিল।
বর্তমান প্রবন্ধে আলোচ্য প্রশ্নের জওয়াব দিতে চেষ্টা করা হইয়াছে। এই প্রবন্ধে হযরত আবূ বকর (রা)-এর চরিত্র-বৈশিষ্ট্য ও অতুলনীয় জনহিতকর কাজকর্ম সম্পর্কে আলোকপাত করা হইয়াছে। পূর্ণাঙ্গ ইসলামী সমাজে নেতৃত্বের যে শ্রেষ্ঠত্ব ও উচ্চতর মর্যাদা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর লাভ করিয়াছিলেন, তাহা লক্ষ্য করিয়াই হযরত উমর ফারুক (রা) অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক কণ্ঠে বলিয়াছিলেনঃ
শ্রেষ্ঠত্ব ও খিলাফতের সঠিক মাপকাঠি যদি ইহাই হয়, তাহা হইলে আপনার পরবর্তী খলীফাগণ তো কঠিন অসুবিধান পড়িয়া যাইবেন,কেননা আপনার সমকক্ষতা অর্জন করা কাহারো পক্ষে সম্ভব হইবে না।
পবিত্র স্বভাব-প্রকৃতি
হযরত আবূ বকর (রা)-এর জীবন চরিত আলোচনা করিলে সর্বপ্রথম আমাদের সম্মুখে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে তাঁহার হৃদয়-মনের পবিত্রতা,পরিশুদ্ধতা এবং নির্মলতা। এই কারণে ইসলাম ও নবী করীম (স)-কে সঠিক রূপে চিনিয়া লইতে তাঁহার বিশেষ কোন অসুবিধা বা বিলম্ব হয় নাই। তাঁহার সম্মুখে ইসলামের দাওয়াত ও হযরতের নবুয়্যাত পেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি উহা অকুণ্ঠিত চিত্তে গ্রহণ করিয়াছেন। কোন সংশয়, কোন দ্বিধা অথবা কোন শ্রেষ্ঠত্ববোধের জাহিলিয়াত আসিয়া এই পথে একবিন্দু প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করিতে পারে নাই। হযরত আবূ বকর (রা) তদানীন্তন সমাজের সম্মানিত ও শ্রদ্ধাভাজন লোক ছিলেন এবং একজন সম্মানিত ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির পক্ষে অপর কাহারো নেতৃত্ব মানিয়া লইতে যে পর্বত-প্রমাণ বাধার সম্মুখীন হইতে হয়, তাহা এক মনস্তাত্ত্বিক সত্য। কিন্তু হযরত আবূ বকর (রা)-কে এই ধরনের কোন বাধার সম্মুখীন হইতে হয় নাই। ইহা হইতে সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, তিনি একজন সম্মানিত ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও নেতৃত্বের অহংকার ও সম্মানের অহমিকাবোধ হইতে তাঁহার হৃদয়-মন ছিল অত্যন্ত পবিত্র।
তিনি ছিলেন স্বভাবগতভাবে অত্যন্ত সূক্ষ্মদর্শী ও সমালোচকের দৃষ্টিসম্পন্ন প্রাজ্ঞ ব্যক্তি। তাঁহার জাহিলী যুগের জীবন সাক্ষ্য প্রদান করে যে, সমালোচনার কষ্টি-পাথরে যাঁচাই-পরখ না করিয়া কোন বিষয়কে তিনি গ্রহণ করিতে কখনো প্রস্তুত ছিলেন না। কাজেই ইসলাম ও হযরতের নবুয়্যাতের প্রতি নিছক অন্ধভাবে বিশ্বাস স্থাপন করাও তাঁহার পক্ষে কিছুতেই সম্ভবপর ছিল না। এতৎসত্ত্বেও অনতিবিলম্বে ইসলাম কবুল করার একমাত্র কারণ এই যে, অসাধারণ মানসিক পবিত্রতা ও প্রকৃতির স্বচ্ছতার কারণে হযরতের সত্তবাদিতা ও তাঁহার কথাবার্তার যথার্থতা সম্পর্কে তাঁহার মন ছিল দিবালোকের মতই উজ্জ্বল ও উদ্ভাসিত। এই জন্যই ইসলামকে তিনি আপন মনের প্রতিধ্বনি হিসাবেই গ্রহণ করিয়াছেন। হযরত আবূ বকর (রা) সম্পর্কে জাহিলী সমাজের প্রভাবশালী ব্যাক্তি ইবনূদ দাগনা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঘোষণা করিয়াছিলঃ “তুমি নিকট-আত্মীয়দের হক আদায় কর, সদা সত্য কথা বল, অভাবী লোকদের অভাব পূরণ কর, আহত,নির্যাতিত ও বিপদগ্রস্ত লোকদের তুমি সাহায্য কর”-এইরূপ ব্যক্তির স্বচ্ছ হৃদয়-পটে যে কোন প্রকার মালিন্য পুঞ্জিভূত হইতে পারে না এবং রাসূলের সত্যতা স্বীকার করিতে ও ইসলাম গ্রহণ করিতে একবিন্দু বিলম্ব হইতে পারে না, তাহা বলাই বাহুল্য। এইরূপ পবিত্র আত্মা ও স্বচ্ছ মনের অধিকারীর জন্য পয়গাম্বরের দাওয়াত ও তাঁহার উজ্জ্বল মুখমণ্ডল অনেকটা মুজিজার সমতুল্য। সত্যের আওয়াজ শোনামাত্রই তাহার চৈতন্য জাগ্রত হইয়া উঠে, হৃদয় অবনমিত হয়। বিশ্বনবী নিজেই হযরত আবূ বকর (রা)-এর এই গুন –বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সাক্ষ্যদান প্রসঙ্গে স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেনঃ
আমি যাহাকেই ইসলামের দাওয়াত দিয়াছি, প্রত্যেকেই ইসলাম কবুল করার ব্যাপারে কিছু দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও সংকোচ অনুভব করিয়াছে। কিন্তু আবূ বকর বিন আবূ কোহফা ইহার ব্যতিক্রম। আমি যখনি তাঁহার সম্মুখে এই কথা পেশ করিলাম তখন উহা কবুল করিতে যেমন তাহাকে কোন প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হইতে হয় নাই, তেমনি এই ব্যাপারে তিনি বিন্দুমাত্র ইতস্ততাও বোধ করেন নাই।
হযরত আবূ বকর (রা) তাঁহার অনন্য পবিত্র স্বভাব-প্রকৃতির দরুণ অসংখ্য পবিত্র স্বভাববিশিষ্ট ও সৎকর্মশীল লোকদিগকে নিজের চতুস্পাের্শ্ব একত্রিত করিয়া লইয়াছিলেন। তাহারা আবূ বকর (রা)- এর চরিত্র-বৈশিষ্ট্য ও গুন গরিমার জন্য তাঁহার প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট ছিল। জীবনের সকল গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারেই তাঁহার সিদ্ধান্তকে তাহার অকুণ্ঠিত চিত্তে মানিয়া লইত। তাহারা যখন দেখিতে পাইল যে, হযরত আবূ বকর (রা) ইসলাম কবুল করিয়াছেন, তখন তাহারা এই বিচক্ষণ সহযাত্রী ও আস্থাভাজন নেতার সিদ্ধান্তে অনুপ্রাণিত না হইয়া পারিল না। ফলে তাহাদেরও ইসলাম কবুল করিতে বিশেষ বিলম্ব হইল না।হযরত উসমান বিন আফফান, আবদুর রহমান বিন আউফ, তালহা বিন উবাইদুল্লাহ, সায়াদ বিন আবী অক্কাস, জুবাইর বিন আওয়াম ও আবু উবাইদাহ বিন জাররাহ ন্যায় বিরাট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন লোকেরা হযরত আবূ বকর (রা)-এর দাওয়াতেই ইসলাম কবুল করিয়াছিলেন এবং এই মহান ব্যক্তিদের কারণে ইসলামী আন্দোলন প্রথম পর্যায়েই অত্যন্ত শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। ইঁহাদের এক একজন ছিলেন আপন যোগ্যতা ও কর্মক্ষমতার দিক দিয়া ইসলামের অপূর্ব সম্পদ আর এই ধরনের লোকদিগকে যে মহান ব্যক্তি ইসলামে দীক্ষিত করিয়াছিলেন, তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব ও বিরাটত্ব ভাষায় বলিয়া শেষ করা যায় না।
নৈতিক বল ও অসমসাহস
দুনিয়ায় আল্লাহ্র কালেমা প্রচার ও দ্বীন-ইসলামের পতাকা উড্ডীন করার জন্য হযরত আবূ বকর (রা)-এর নৈতিক বল ও অসম সাহসিকতা এক তুলনাহীন ব্যাপার। তিনি যে একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি এবং ব্যবসায়ী ছিলেন, তাহা সর্বজনবিদিত। একজন নেতার পক্ষে অপর কাহারো নেতৃত্ব স্বীকার করিয়া স্বীয় নেতৃত্বের পক্ষে বিপদ টানিয়া আনা অত্যন্ত কঠিন কাজ। উপরন্তু যে আন্দোলন যোগদান করার ফলে জনগণের নিকট ধিকৃত ও তিরস্কৃত হইতে হয় এবং যাহার পরিণতিতে নিজের ব্যবসায় বিনষ্ট হইতে পারে, তাহা কবুল করা দূরন্ত সাহস ও হিম্মতের উপর নির্ভর করে। কেননা তাহাতে বৈষয়িক স্বার্থ তথা রুজি-রোজগার কঠিনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে। অন্ততঃসাধারণ ও ছোট মনের ব্যবসায়ীদের খুব বেশী দ্বারা এই কাজ কিছুতেই সম্পন্ন হইতে পারে না। এ ব্যাপারে কোন ব্যবসায়ী খুব বেশী দুঃসাহসের পরিচয় দিলেও এতটুকুই তাঁহার নিকট আশা করা যাইতে পারে যে, সে নিজ পছন্দমত কোন আন্দোলনকে অন্তর দিয়া সমর্থন করিবে ও যথাসম্ভব উহাকে আর্থিক সাহায্য দান করিবে; কিন্তু নীতিগতভাবে কোন আন্দোলনকে মন-মগজ দিয়া মানিয়া লওয়া এবং কার্যতঃউহার আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রবল প্রতিকূল শক্তির সহিত সর্বাত্মক সংগ্রামে লিপ্ত হওয়া, উপরন্তু স্বীয় ব্যবসায় ও রুজী-রোজগারকে কঠিন বিপদের মুখে ঠেলিয়া দেওয়ার মত দুঃসাহস খুব কম লোকেই করিতে পারে। কিন্তু হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) এইরূপ দুঃসাহস পূর্ণমাত্রায় প্রদর্শন করিয়াছেন। অতঃপর যে সব দুঃসাহসী অভিযাত্রী এই বিপদ-সংকুল পথে পদক্ষেপ করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলেরই সম্মুখে একমাত্র আদর্শ ছিল হযরত আবূ বকর (রা)-এর অপূর্ব বিপ্লবী ভূমিকা।১ {আর্থিক কুরবানীর অনন্য দৃষ্টান্তঃইসলামের প্রতিষ্ঠা ও প্রতিরক্ষা এই উভয় কার্যেই অর্থ ব্যয় করিতে হযরত আবূ বকর (রা) ছিলেন অত্যন্ত উদারহস্ত। এই ব্যাপারে সাহাবায়ে কিরামের গোটা জামায়াতের মধ্যে তাঁহার ভূমিকা ছিল অতুলনীয়-অনুকরণীয়। রাসূলে করীম (স) যখনই কোন কাজে সাহাবাদের নিকট আর্থিক কুরবানীর আহ্বান জানাইয়াছেন, হযরত আবূ বকর (রা) তখনই সর্বোচ্চ ত্যাগের মনোভাব লইয়া আগাইয়া আসিয়াছেন। তবুক অভিযানকালে রাসূলে করীম (স) সাহাবাদের নিকট সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারের আহ্বান জানাইলে একমাত্র আবূ বকর (রা) তাঁহার সমগ্র বিত্ত-সম্পদ আল্লাহ্র রাহে দান করিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, সমগ্র বিত্ত-সম্পদ দান করিয়া দিলে তাঁহার পরিবার পরজনের ভরণপোষণ কিভাবে চলিবে? জওয়াবে তিনি বলিলেনঃ ‘তাঁহাদের জন্য আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলই যথেষ্ট’। হযরত আবূ বকর (রা) আল্লাহ্র রাহে কতখানি নিবেদিতচিত্ত ছিলেন,তাঁহার আর্থিক কুরবানীর এই অনন্য দৃষ্টান্ত হইতেই তাহা গভীরভাবে উপলব্ধি করা যায়।–সম্পাদক}
মজলুমকে সাহায্য ও সমর্থন দান
ইসলামী আন্দোলনকে প্রাথমিক পর্যায়ের কঠোর অগ্নিপরীক্ষাকালে সত্যপথের মজলুমদিগকে ইসলামের দুশমনদের নির্যাতন হইতে রক্ষা করার ব্যাপারে হযরত আবূ বকর (রা)-এর অর্থসম্পদ যে বিরাট কাজ করিয়াছে, ইতিহাসে তাঁহার দৃষ্টান্ত বিরল। বিলাল হাবশী (রা) ও ইবনে ফুহাইরা (রা)—র মত ক্রীতদাস শ্রেণীর লোক ইসলাম কবুল করার অপরাধে স্বীয় মালিক-মনিবদের অত্যাচার-নিষ্পেষণে নিতান্ত অসহায়ের মত নিষ্পেষিত হইতেছিল। হযরত আবূ বকর (রা)-এর সৌহার্দ্য ও দানশীলতার-দৌলতে তাঁহারা এই দুঃসহ আযাব হইতে নিষ্কৃতি লাভ করেন। এইজন্য তাঁহাকে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করিতে হইয়াছে। এই খাতে তাঁহাকে যে কী পরিমাণ অর্থ ব্যয় করিতে হইয়াছে, একটি ব্যাপার দ্বারাই সে সম্পর্কে অনুমান করা যাইতে পারে। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)যখন ইসলাম কবুল করেন,তখন তাঁহার নিকট চল্লিশ হাজার দিরহাম নগদ অর্থ সঞ্চিত ছিল; কিন্তু বারো-তেরো বৎসর পর যখন তিনি মদীনায় হিজরত করেন,তখন তাঁহার নিকট মাত্র পাঁচ হাজার দিরহাম অবশিষ্ট ছিল। অথচ এই দীর্ঘ সময়ে তাঁহার ব্যবসায়ে অত্যন্ত সাফল্যজনকভাবে চলিয়াছে এবং তাহাতে প্রচুর মুনাফা অর্জিত হইয়াছে।২ {রাষ্ট্রীয় তহবিলের আমানতদারীঃখিলাফতের প্রশাসনিক ক্ষমতার ন্যায় রাষ্ট্রের অর্থ-সম্পদকে হযরত আবূ বকর (রা)এক বিরাট আমানত রূপে গণ্য করিতেন। জীবিকা নির্বাহের জন্য তিনি ব্যবসা-বাণিজ্য করিতেন বলিয়া প্রথম দিকে তিনি রাষ্ট্রীয় তহবিল হইতে কোন বেতন-ভাতাই নিতেন না। কিন্তু পরবর্তীকালে খিলাফতের কার্যে সার্বক্ষণিক ব্যস্ততার ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য অচল হইয়া পড়ায় তিনি রাষ্ট্রীয় তহবিল হইতে একজন সাধারণ নাগরিকের ন্যায় নামমাত্র ভাতা গ্রহণ করিতে শুরু করেন। ইহাতে তাঁহার পরিবার-পরিজনের ভরণ-পোষণের কাজ কোন প্রকারে চলিয়া যাইত। এই পরিস্থিতিতে কিছু কিছু খাদ্য-সামগ্রী বাঁচাইয়া একদা তাঁহার স্ত্রী একটি মিষ্টি খাবার তৈয়ার করেন। খলীফা অবাক হইয়া স্ত্রীকে প্রশ্ন করিলে তিনি নিয়মিত বরাদ্দ হতে কিছু কিছু খাদ্য বাচাইবার কথা খুলিয়া বলেন। ইহা শুনিয়া খলীফা মন্তব্য করেনঃযে পরিমাণ খাদ্য বাঁচাইয়া তার মিষ্টি তৈয়ার করা হইয়াছে,উহা আমাদের না হইলেও চলে। কাজেই ভবিষ্যতে বায়তুল মাল হইতে ঐ পরিমাণ খাদ্য কম আনা হইবে। রাষ্ট্রীয় তহবিলের আমানতদারীর ব্যাপারে তিনি কতখানি সতর্ক ছিলেন, এই ঘটনা হইতেই তাহা প্রমাণিত হয়।–সম্পাদক}
হযরতের জন্য আত্মোৎসর্গ
বিশ্বনবীর ইসলামী দাওয়াত ও আন্দোলনের প্রাথমিক কাল হইতে শুরু করিয়া কঠোর বিপদ-মুসীবতের শেষ পর্যায় অবধি হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) তাঁহার জন্য আত্মোৎসর্গকৃত ও নিবেদিতচিত্ত হইয়া রহিয়াছেন। কুরাইশগণ যখনই বিশ্বনবীকে কোন প্রকার জ্বালা-যন্ত্রণা দিতে চেষ্টা করিয়াছে,হযরত আবূ বকর সিদ্দীক(রা) তখনই স্বীয় প্রাণ ও ইজ্জত বিপন্ন করিয়া তাঁহার সাহায্য-সহযোগিতায় আগাইয়া আসিয়াছেন এবং সম্মুখে অগ্রসর হইয়া প্রত্যাসন্ন বিপদের মুকাবিলা রহিয়াছেন। ইসলামী দাওয়াতের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা ও অগ্রগতির প্রত্যক্ষ আঘাতে যে সব নেতৃস্থানীয় লোকের মাতব্বরী ও নেতৃত্ব বিপন্ন হইয়াছিল, তাহারা একদিন কোন এক স্থানে একত্রিত হইয়া পারস্পরিক পরামর্শ করিতেছিল এবং আসন্ন বিপদ হইতে আত্মরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের উপায় নির্ধারণের ব্যতিব্যাস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহারা সকলেই ভয়ানক ক্রুদ্ধ,রুষ্ট ও আক্রোশান্ধ। ঠিক এই সময় নবী করীম (স) সেখানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। ইসলামের এই দুশমন লোকগুলি তাঁহার উপর হটাৎ আক্রমণ করিয়া বসিল। তাহারা বলিলঃ ‘তুমিই তো আমাদের ধর্ম ও আমাদের উপাস্য দেবতাদের তিরস্কার ও ভৎসনা কর”। নবী করীম (স) উত্তরে বলিলেন, “হ্যাঁ আমিই তাহা করি”। সহসা একটি লোক হযরতের চাদর আঁকড়াইয়া ধরিল ও তাঁহাকে কঠিন আঘাত হানার উদ্দেশ্যে হস্ত প্রসারিত করি। তৎক্ষণাৎ হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) সেখানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি ইহাদের বদমতলব বুঝিতে পারিলেন। তিনি সমস্ত বিপদের ঝুঁকি নিজের মস্তকে লইয়া সম্মুখে অগ্রসর হইলেন ও ক্রুদ্ধ স্বরে বলিয়া উঠিলেনঃ “তোমরা কি একটি লোককে শুধু এই অপরাধেই হত্যা করিতে চাও যে, সে কেবল এক আল্লাহ্কেই নিজের রব্ব বলিয়া ঘোষণা করে?”
হিজরতের কঠিন মুহূর্তে নবী করীম (স) হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-কেই সহযাত্রীরূপে গ্রহণ করিলেন। হযরতের এই সফর ছিল অত্যন্ত বিপদসংকুল এবং যে কোন মুহূর্তে তাঁহার জীবন বিপন্ন হইতে পারে-হযরত আবূ বকর (রা) ইহা ভাল করিয়াই জানিতেন। তিনি ইহাও জানিতেন যে, এই সফরে যতখানি বিপদ হযরতের উপর আসার আশংকা ছিল, তাঁহার সহযাত্রীর উপর তাহা অপেক্ষা কম বিপদ আপতিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিলনা। কিন্তু এই সবকিছু সুস্পষ্টরূপে জানিয়া বুঝিয়া লওয়ার পরও তিনি নিজের জন্য বিরাট সৌভাগ্য বলিয়া মনে করিলেন এবং এই সফরে তিনি হযরতের সঙ্গী হইয়া সকল প্রকার বিপদের মুকাবিলা করার সুযোগ পাইবেন বলিয়া আল্লাহ্র শোকরিয়া আদায় করিলেন।
মক্কা হইতে মদীনা যাওয়ার পথে এই ক্ষুদ্র কাফেলা প্রথমে আশ্রয় গ্রহণ করে ‘সাওর’ নামক পর্বত গুহায়। এই গুহায় প্রবেশ করিবার সময় হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)নবীগতপ্রাণ হওয়ার বাস্তব প্রমাণ উপস্থাপিত করেন। জনমানব বিবর্জিত শ্বাপদসংকুল পর্বত গুহায় সর্বপ্রথম হযরত আবূ বকর (রা)নিজে প্রবেশ করিয়া উহাকে পরিষ্কার করেন। উহার অসংখ্য ছিদ্রপথ বন্ধ করিয়া দেন। নবী করীম (স) এই গুহায় আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর জানুর উপর মস্তক স্থাপন করিয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন। এমন সময় একটি উন্মুক্ত ছিদ্রমুখ হইতে এক বিষধর সর্প বাহির হইয়া হযরত আবূ বকর (রা)-এর পায়ে দংশন করে। আবূ বকর (রা) বিষক্রিয়ায় জর্জরিত হইয়া পড়েন; কিন্তু হযরতের নিদ্রাভঙ্গ ও তাঁহার বিশ্রামে ব্যাঘাত সৃষ্টির ভয়ে তিনি একবিন্দু নড়াচড়া করেন নাই। কিন্তু বিষের দুঃসহ ব্যাথা তাঁহাকে এতদূর কাতর করিয়া ফেলে যে, তাঁহার চক্ষু কোটর হইতে দুই ফোঁটা অশ্রু-বিগলিত হইয়া রাসূলের গণ্ডদেশে পতিত হয়। রাসূল (স)-এর প্রতি কত অসীম ভালবাসা ও আন্তরিক ভক্তি-শ্রদ্ধা থাকার কারণে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) এইরূপ করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা ধারণা করা আমাদের পক্ষে কঠিন ব্যাপার।
কঠোরতা ও কোমলতার অপূর্ব সমন্বয়
হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর চরিত্রে কঠোরতা ও কোমলতার অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়াছিল। ইহা ছিল তাঁহার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য এবং এই কারণে তাহা ছিল নবীর প্রকৃতির সহিত গভীর সামঞ্জস্যপূর্ণ। যেখানে কঠোরতা অবলম্বনের প্রয়োজন হইত, সেখানে তিনি ঠিক প্রয়োজনীয় মাত্রায় ইস্পাতকঠিন হইয়া দাঁড়াইতেন। পক্ষান্তরে যেখানে নম্রতা প্রদর্শন আবশ্যক হইত, সেখানে তিনি অকারণ ক্রোধ ও অন্তঃসারশূন্য আত্মসম্মানবোধের মোটেই প্রশ্রয় দিতেন না। সেখানে তিনি বিগলিত-দ্রবীভূত ধাতুর মত। ফখাচ নামক এক ইয়াহুদী একবার আল্লাহ্র নাম করিয়া বিদ্রুপ করিতেছিল; ইহাতে হযরত আবূ বকর (রা)-এর দেহে প্রবল রোষাগ্নি জ্বলিয়া উঠে। তিনি পূর্ণ শক্তিতে সেই ব্যক্তিকে এক চপেটাঘাত করেন এবং বলেন, “তোমাদের ও আমাদের মধ্যে ‘যুদ্ধ নয়’ চুক্তি স্বাক্ষরিত না হইলে এখনি তোমার মস্তক ছিন্ন করিয়া দিতাম”। হুদাইবিয়ার সন্ধি-চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার সময় কুরাইশ প্রতিনিধিগণ বিদ্রুপ ও উপহাস করিয়া নবী করীম (স)-কে বলিয়াছিলেন যে, কঠিন বিপদের সময় আপনার সঙ্গীরা আপনার সহচর্য ত্যাগ করিবে। তখন হযরত আবূ বকর (রা) অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং এত কঠোর ভাষায় ইহার উত্তর দিয়াছিলেন যে, তাঁহার ন্যায় ধৈর্যশীল ব্যক্তির নিকট হইতে এইরূপ উক্তি সাধারণতঃ ধারণাও করা যায় না। কিন্তু সম্মান ও মর্যাদাবোধ তাঁহার মধ্যে এত তীক্ষ্ণ ছিল যে, ঐরুপ জওয়াব তাঁহার কণ্ঠ হইতে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই নিঃসৃত হইয়াছিল। আর যাহাকে এইরুপ কঠোর ভাষায় উত্তর দান করা হয়, জাহিলিয়াতের যুগে সে ছিল হযরত আবূ বকর (রা)-এর অনুগৃহীত। সেই কারণে লোকটি উহা সহ্য ও হজম করিতে বাধ্য হয়।
অপরদিকে বদর যুদ্ধের সময় আল্লাহ্ যখন মুসলমানদিগকে বিজয় মাল্যে ভূষিত করেন ও বহুসংখ্যক কাফির সরদার বন্দি হইয়া আসে, তখনই তিনি ইহাদের প্রতি স্নেহ-অনুগ্রহের অতল সাগর রূপে নিজেকে তুলিয়া ধরেন;অথচ একথা তিনি এক মুহূর্তের তরেও ভুলিতে পারেন নাই যে, এই সব কুরাইশ সরদারই নিরীহ ও অসহায় মুসলিমদিগকে অত্যাচার-নিষ্পেষণে জর্জরিত করিয়া তুলিয়াছিল, বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (স) এবং তাঁহার সঙ্গী সাথীদের উপর অমানুষিক অত্যাচারের ষ্টীম রোলার চালাইয়াছিল ও তাঁহাদিগকে দেশত্যাগ করিতে বাধ্য করিয়াছিল। স্বয়ং হযরত আবূ বকর (রা)ও নানাভাবে ইহাদের হাতে নির্যাতিত ও নিপীড়িত হইয়াছিলেন। কিন্তু ইসলামের জন্য এই সবকিছুই তিনি অবলীলাক্রমে বরদাশত করেন। তথাপি এই করায়ত্ত লোকদের নিকট হইতে তিনি একবিন্দু প্রতিশোধ লওয়ার কথা চিন্তা করিতে পারেন নাই। সেইজন্য অপরাপর সাহাবীদের ন্যায় তিনি বিশ্বনবীকে বন্দীদের হত্যা করার পরামর্শ না দিয়া তাহাদিগকে বিনিময় গ্রহণপূর্বক মুক্ত করিয়া দিবারই পরামর্শ দিলেন। মুসলমানদের তরফ হইতে এই অপ্রত্যাশিত অনুগ্রহ লাভ করিয়া কাফির সরদারগন হয়তবা ইসলামের দিকে আকৃষ্ট হইবে ও আল্লাহ্র সন্তোষ লাভে উদ্যোগী হইবে, ইহাই ছিল হযরত আবূ বকর (রা)-এর বিশ্বাস ও প্রত্যাশা।
দূরদৃষ্টি ও বিচক্ষণতা
হুদাইবিয়ার সন্ধি ইসলামী ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। যে পরিস্থিতিতে ও যে সব শর্তের ভিত্তিতে এই চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছিল, তাহা দৃশ্যতঃমুসলমানদের পক্ষে ছিল অত্যন্ত নৈরাশ্যব্যঞ্জক ও মর্মবিদারক। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইহার যে পরিণতি দেখা গিয়াছিল, তাহা ইসলাম ও মুসলমানদের পক্ষে শুধু বিপুল উদ্দীপকই ছিল না, প্রকৃত পক্ষে তাহা ছিল মুসলমানদের জন্য ‘ফতহুমমুবীন-সুস্পষ্ট বিজয়। এই সন্ধি চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার সময় হযরত আবূ বকর (রা)-এর ভূমিকা তাঁহার সূক্ষ্ম দূরদৃষ্টি,তীক্ষ্ণ বিচার-বুদ্ধি ও বিপুল প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের অনস্বীকার্য পরিচয় বহন করে। এই সন্ধির শর্তসমূহ একজন সাহাবীও গ্রহণ করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। হযরত উমর ফারুক (রা)সংশ্লিষ্ট শর্তসমূহের এতদূর বিরোধী ছিলেন যে, তিনি রাসূলের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া অত্যন্ত কঠোর ভাষায় কথাবার্তা বলিয়াছিলেন।(এজন্য অবশ্য আজীবন তিনি অনুতাপ করিয়াছেন)। কেবলমাত্র হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)ই এই ব্যাপারে আগাগোড়া রাসূলের সমর্থক ছিলেন। তিনি কেবল পূর্ণ শক্তিতে এই সন্ধি-চুক্তিকে সমর্থনই করেন নাই, স্বীয় প্রভাব খাটাইয়া অন্যান্য মুসলিমদেরও নিশ্চিন্ত করিয়াছিলেন। এইসব চেষ্টার ফলেই শেষ পর্যন্ত হযরত উমর ফারুক (রা)-এর অসন্তোষ প্রশমিত হয়।
বস্তুতঃযে সন্ধি চুক্তি প্রকাশ্যভাবে ও বাহ্যদৃষ্টিতে মুসলমানদের পক্ষে ক্ষতিকর ছিল-তাহাদের মর্যাদার পক্ষে ছিল হানিকর ও ভবিষ্যতের জন্য অন্ধকারের ইঙ্গিতবহ এবং যে কারণে গোটা মুসলিম সমাজের মদ্য হইতে একব্যক্তিও উহার সমর্থক ও সে সম্পর্কে নিঃসংশয় ছিল না, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) উহার সুফল প্রকাশিত হওয়ার কয়েক বৎসর পূর্বেই আপন জ্ঞানচক্ষু দ্বারা উহার সুদূরপ্রসারী কল্যাণকারিতা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। স্বয়ং নবী করীম (স) তো অহী ও ইলাহামের সাহায্যে হুদাইবিয়া সন্ধির অন্তর্নিহিত কল্যাণকারিতা ও বিরাট সুফল সম্পর্কে পূর্ণ অবহিত ছিলেন এবং এই জন্য ছিলেন দৃঢ় প্রত্যয়-অচল-অটল। কিন্তু হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)ঐরূপ সাহায্য ছাড়াই এ সম্পর্কে যে সমর্থন ও দৃঢ়টা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা বাস্তবিকই বিস্ময়কর। ইহা যদি ঈমানের স্বতঃস্ফূর্ত আলোক প্রভাব সফল হইয়া থাকে তবে বলিতেই হইবে যে, এইরূপ ঈমান-ঈমানের এই সুউচ্চতম মান একমাত্র আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এরই অর্জিত ছিল। আর রাজনৈতিক অন্তর্দৃষ্টি ও বিচক্ষণতার দৌলতে সন্ধির অন্তর্নিহিত ইতিহাসে ইহার বাস্তবিকই কোন তুলনা পাওয়া যাইবে না।
আল্লাহ্, রাসূল ও মুসলিমদের নিকট সমান প্রিয়পাত্র
হযরত আবূ বকর (রা) তাঁহার ঐকান্তিক ও নিষ্ঠাপূর্ণ খিদমতের কারণে আল্লাহ্, রাসূল ও মুসলিম জনগণের নিকট সমান প্রিয়পাত্র ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে এই জনপ্রিয়তার মর্যাদা এতদূর উন্নত ছিল যে, বিশ্বনবীর পর অন্য কেহই এই ক্ষেত্রে তাঁহার সমতুল্য ছিল কিনা সন্দেহ। ইসলামের ইতিহাসের ইহার কোন দৃষ্টান্ত খুঁজিয়া পাওয়া যায়না। এইখানে উহার কয়েকটি কারণের উল্লেখ করা যাইতেছে।
নবী করীম (স) যখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত ছিলেন,তখন লোকদের নামায পড়াইবার দায়িত্ব তিনি হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর উপর অর্পণ করেন।এ ব্যাপারে অন্যান্যদের সম্পর্কে হযরতকে যেসব পরামর্শ দেওয়া হয়,তিনি তাহা সবই অত্যন্ত দৃঢ়তা সহকারে প্রত্যাখ্যান করেন। ফলে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর উপর অর্পণ করেন। এই ব্যাপারে অন্যান্যদের সম্পর্কে হযরতকে যেসব পরামর্শ দেওয়া হয়, তিনি তাহা সবই অত্যন্ত দৃঢ়তা সহকারে প্রত্যাখ্যান করেন। ফলে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) রীতিমত নামায পড়াইতে থাকেন। একদা তিনি ঠিক সময় মসজিদে উপস্থিত হইতে পারেন নাই বলিয়া হযরত বিলাল (রা) হযরত উমর ফারুক (রা)-কে নামাযে ইমামত করিতে অনুরোধ জানান। নামাযের দেরী হওয়ার আশংকায় হযরত উমর ফারুক (রা) নামায পড়াইতে শুরু করেন। তাঁহার কণ্ঠস্বর ছিল অত্যন্ত উচ্চ ও দূরপ্রসারী। তাঁহার তকবীর ধ্বনি মসজিদ-সংলগ্ন হুজরা মুবারকে শায়িত বিশ্বনবীর কর্ণকূহরে প্রবিষ্ট হইতেই তিনি চকিত হইয়া উঠিলেন ও জিজ্ঞাসা করিলেন, আজ আবূ বকর কোথায়......... এই ব্যাপারটি না আল্লাহ্ পছন্দ করিবেন আর না মুসলিম জনগণ।
শুধু তাহাই নয়, বিশ্বনবীর দৃষ্টিতে হযরত আবূ বকর (রা)-এর যে অপূর্ব মর্যাদা ও আস্থা ছিল, তাহাও অতুলনীয়। নবী করীম (স)নিজেই তাঁহার এক বানীতে সুস্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেনঃ
সমগ্র সাহাবীর মধ্যে তাঁহার ন্যায় অনুগ্রহ আর কাহারো নাই। মানব সমাজের কাহাকেও যদি আমি বন্ধুরুপে বরণ করিতাম,তাহা হইলে আবূ বকর (রা) কেই আমার বন্ধু বানাইতাম। অবশ্য আমাদের বন্ধুত্ব,সাহচর্য্য,ভ্রাতৃত্ব ও ঈমানের দৃঢ় সম্পর্ক বিদ্যমান রহিয়াছে এবং ইহা থাকিবে ততদিন,যতদিন না আল্লাহ্ আমাদিগকে পুনরায় একত্রিত করেন।(বুখারী)
বিশ্বনবীর দরবারে হযরত আবূ বকর (রা)-এর যে কতখানি মর্যাদা ছিল, তাহা রাসূলের জীবনব্যাপী কর্মধারা হইতে সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায়। মক্কা শরীফে নবী করীম (স) প্রায়শঃহযরত আবূ বকর (রা)-এর ঘরে যাতায়াত করিতেন। মদীনা শরীফেও অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারেই তাঁহার উপস্থিতি অপরিহার্য ছিল। একদিন তিনি নিজ ঘরে তিনজন দরিদ্র সাহাবীকে খাওয়ার দাওয়াত দিয়াছিলেন;কিন্তু অধিক রাত্র পর্যন্ত তিনি রাসূলের দরবারে বিশেষ জরুরী কাজে এমনভাবে আটক ছিলেন যে, যথাসময়ে ঘরে ফিরিয়া মেহমানদারী করিতে পারেন নাই। হযরত উমর ফারুক (রা) নিজেই বলিয়াছেন যে, হযরত আবূ বকর (রা) ছিলেন বিশ্বনবীর নিত্য-সহচর। মুসলমানদের যাবতীয় সামগ্রিক ও তামাদ্দুনিক ব্যাপারে তাঁহার সাহায্য ও পরামর্শ অত্যন্ত জরুরী ছিল। অনেক গোপন বিষয় সম্পর্কেই তিনি অবহিত হইতেন। হযরতের ইন্তেকালের পূর্বে মসজিদের চৌহদ্দির মধ্যে যতগুলি দ্বার রক্ষিত ছিল,তন্মধ্যে কেবলমাত্র আবূ বকর (রা)-এর দরজা ব্যতীত আর সবই বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। নবী করীম (স)-কে কখনো অস্বাভাবিক রূপে রাগান্বিত দেখিলে সাহাবায়ে কিরাম হযরত আবূ বকর (রা)-এর মাধ্যমেই প্রকৃত ব্যাপার সম্পর্কে অবহিত হইতেন এবং প্রয়োজন হইলে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেন।
চরিত্র বৈশিষ্ট্য
হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) স্বভাবতঃই উন্নত ও মহৎ চরিত্রে বিভূষিত ছিলেন। জাহিলিয়াতের যুগেও পবিত্রতা,সততা, দয়াশীলতা, অনুগ্রহ, ন্যাপরায়ণতা ও বিশ্বাসপরায়ণতার গুণে তিনি গুণান্বিত ছিলেন। তদানীন্তন সমাজে তিনি ছিলেন একজন আমানতদার ব্যক্তি। যে সমাজে মদ্যপান,ব্যাভিচার ও ফিসক-ফুজুরী সর্বগ্রাসী রূপে ধারণ করিয়াছিল,আবূ বকর সিদ্দীক (রা)সেই সমাজের একজন মর্যাদাবান লোক হওয়া সত্ত্বেও উহার সমস্ত কলুষতা ও পঙ্কিলতা হইতে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণরূপে পবিত্র। বস্তুতঃএই গুনগুলি তাঁহার মধ্যে স্বভাবগতভাবেই বর্তমান ছিল। উত্তরকালে কুরআনের নৈতিক শিক্ষা ও হযরতের ঘনিষ্ঠ সাহচর্যের ফলে এই গুণগুলি তাঁহার চরিত্রে অধিকতর চমকিত হইয়া উঠে।
কাহারো মধ্যে তাকওয়া পূর্ণ পরিণত হইয়া উঠে তখন, যখন একদিকে তাহার মন-মগজ সকল প্রকার বাতিল চিন্তা ও মতাদর্শ হইতে মুক্ত এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সকল অন্যায় ও পাপ কাজ হইতে বিরত হয়। বিশ্বনবীর পরে এই রূপ তাকওয়া হযরত আবূ বকর (রা)-এর চরিত্রে যত প্রকটভাবে পরিলক্ষিত হয়, তত আর কাহারো মধ্যে নয়।
নেতৃত্ব,কর্তৃত্ব,মাতব্বরি,দুনিয়া-প্রীতি ও সম্মান-স্পৃহার প্রতি হযরত আবূ বকর (রা)স্বভাবতঃই ঘৃণাবোধ করিতেন। তিনি তাঁহার ধন-সম্পদ আল্লাহ্র পথে অকাতরে ও উদার-উন্মক্ত হতে ব্যয় করিয়াছেন। এমন কি খিলাফতের যুগে তিনি ছয় হাজার দিরহাম ঋণী হইয়া পড়েন। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও তিনি জনগণের একটি ক্রান্তি পরিমাণ অর্থ নিজের জন্য ব্যয় করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। তাই ইন্তেকালের পূর্বে তাঁহার নিজস্ব বাগান বিক্রয় করিয়া বায়তুলমালের ঋণ শোধ করার অসীয়াত করিয়া অর্থ উদ্ধৃত্ত যাহা কিছু থাকিলে,তাহা পরবর্তী খলীফার নিকট পাঠাইয়া দেওয়ার উপদেশ দেন।
দৃঢ়তা ও স্থিরতা
হযরত আবূ বকর (রা)-এর জীবনে সর্বাধিক কঠিন বিপদ ও অগ্নিপরিক্ষা দেখা দেয় বিশ্বনবীর ইন্তেকালের সময়।আঁ-হযরতের প্রতি তাঁহার যে দরদ ও আকর্ষণ ছিল, উহাকে ‘প্রেমের’ পর্যায়ভুক্ত বলা যাইতে পারে। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও তিনি বিশ্বনবীর ইন্তেকালের সংবাদ শ্রবণ করিয়া যে অপরিসীম ধৈর্য ও স্থৈর্যের পরিচয় দান করিয়াছিলেন, ইতিহাসে উহার তুলনা বিরল।শুধু তাহাই নয়,ইসলামের এই কঠিন মুহূর্তে হযরত আবূ বকর (রা)-এর অচল-অটল দৃঢ়তা ও প্রবল স্থিরতা যদি মুলিমদিগকে সঠিক পথ নির্দেশ না করিত,তাহা হইলে গোটা উম্মতে মুসলিমাই যে এক কঠিন ও সর্বাত্মক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হইত তাহাতে সন্দেহের লেশমাত্র নাই। বস্তুতঃআঁ-হযরতের ইন্তেকালের সংবাদ পাইয়া সর্বসাধারণ মুসলমান অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়ে,অনেকে দিগ্বিদিক জ্ঞান হারাইয়া ফেলে। হযরত উমর (রা)-এর ন্যায় বলিষ্ঠ ও পরিচ্ছন্ন দিল-দিমাগের অধিকারী লোকও এতদূর বিহবল হইয়া পড়েন যে, মসজিদে নববীতে দাঁড়াইয়া মুসলিম জনসাধারণকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বক্তৃতা করিতে লাগিলেন যে,আঁ-হযরত (স) ইন্তেকাল করেন নাই,বরং হযরত মূসা যেমন চল্লিশ দিনের জন্য আল্লাহ্র নিকট চলিয়া গিয়াছিলেন এবং পুনরায় প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন, হযরত মুহাম্মাদ(স)ও অনুরুপভাবে নিকট চলিয়া গিয়াছেন, আবার তিনি ফিরিয়া আসিবেন। এমনকি যদি কেহ বলিত যে, হযরত ইন্তেকাল করিয়াছেন,তাহা হইলে তিনি তাহাকে রীতিমত খুন করার ভীতি প্রদর্শন করিতেন এবং বলিতেন যে, নবী করীম (স) আবার ফিরিয়া আসার পর এইরূপ উক্তিকারীদের কঠিন শাস্তি দান করা হইবে।
বস্তুতঃযে কঠিন দুর্ঘটনার ফলে হযরত উমর ফারুক (রা)-এর মন-মগজে এতখানি তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছিল, তাহা অন্যান্য সাহাবীদের উপর কত দুঃসহ হইয়াছিল, উহার সঠিক ধারণা করা সম্ভব নয়। উপরন্তু বিশ্বনবীর চিরন্তন সহচর হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর উপর হযরতের ইন্তেকাল সংবাদের কি সাংঘাতিক প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে, উহার কিঞ্চিৎ হত আঁচ করা যাইতে পারে। বিশেষতঃ হযরত আবূ বকর (রা) সম্পর্কে যখন একথা জানাই আছে যে, নবী করীম (স)-এর সামান্য কষ্টেও তিনি অস্থির হইয়া পড়িতেন,তখন তাঁহার মৃত্যু সংবাদ যে তাঁহার নিকট কতখানি মর্মান্তিক হইতে পারে, তাহা ভাবিলেও শরীর শিহরিতে উঠে। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) বিশ্বনবীর মৃত্যু-সংবাদ শ্রবণ করিয়া কিভাবে ধৈর্যধারণ করেন, কিভাবে এই মর্ম-বিদারী ঘটনার মুকাবিলা করেন এবং কুরআনের আলোকে মুসলিম জনগণকে কিভাবে চরম অন্ধকার হইতে রক্ষা করেন,তাহা সত্যই বিস্ময়কর। হযরতের ইন্তেকালের মুহূর্তে আবূ বকর সিদ্দীক (রা)মদীনা শহরে উপস্থিত ছিলেন না। তিনি ছিলেন মদীনার অদূরে ‘সানাহ’ নামক স্থানে। ইন্তেকালের সংবাদ পাইয়া তিনি দ্রুত শহরে উপস্থিত হইলেন। তিনি সমস্ত মানুষকে দুঃখ-ভারাক্রান্ত ও চিন্তাক্লিষ্ট দেখিতে পাইলেন। আর দেখিলেন হযরত উমর ফারুরুক (রা)কে মসজিদে নববীতে দাঁড়াইয়া বক্তৃতা করিতে। তিনি কোথাও মুহূর্তের জন্য থামিলেন না-সোজা হযরত আয়েশা (রা) ঘরে পৌঁছিলেন ও আঁ হযরতের মুখ-মণ্ডলের আচ্ছাদন সরাইয়া চেহারা মুবারকে চুম্বন দান করিলেন। তিনি হযরতকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেনঃকত মহান পবিত্র ছিলেন জীবনে আর কত পবিত্র আজ মৃত্যুর পর! তিনি সমবেত জনতার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিলেনঃ
যাহারা হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর উপাসনা করিতেছিল তাহাদের জানিয়া রাখা আবশ্যক যে, মুহাম্মাদ (স)মরিয়া গিয়াছেন। আর যাহারা আল্লাহ্র উপাসনা-আরাধনা করিত, তাহাদের এই কথা মনে রাখিতে হইবে যে, আল্লাহ্ চিরদিনের জন্য জিন্দা ও জীবিত, তাঁহার মৃত্যু নাই।
অতঃপর তিনি কুরআন মজীদের এই আয়াত পাঠ করেনঃ
*******(আরবী)
মুহাম্মাদ রাসূল ছিলেন, অন্য কিছু নহেন। তাঁহার পূর্বে আরো অনেক রাসূল গত হইয়াছেন। তিনিও যদি মরিয়া যান কিংবা নিহত হন তবে কি তোমরা পশ্চাদপসরণ করিবে।
হযরত উমর (রা) এই আয়াত শুনিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, রাসূলের ইন্তেকাল নিঃসন্দেহ। যখনি এই অনুভূতি তাঁহার মন-মগজে তীব্রভাবে জাগিয়া উঠিল,তখনি তিনি দুঃখভারে যারপরনাই কাতর হইয়া মাটিতে ঢলিয়া পড়েন। ইহার পর তিনি ও অন্যান্য মুসলিমগণ ব্যাপারটির গভীরতা ও ব্যাপকতা এবং ইহার সুদূরপ্রসারী পরিণতি সম্পর্ককে গভীরভাবে চিন্তা করিতে শুরু করিলেন। বস্তুতঃহযরতের ইন্তেকালে গণমনে যে আঘাত লাগিয়াছিল, তাহাতে প্রায় সকলেরই চিন্তা ও বিবেচনা শক্তি লোপ পাইয়া গিয়াছিল। হযরত আবূ বকর (রা)-এর বক্তৃতার কষাঘাতে ঘনীভূত তমিস্রা অচিরেই শূন্যে বিলীন হইয়া গেল। মুসলিম মিল্লাত ইহা দ্বারা যে কত বড় কঠিন বিপদ হইতে উদ্ধার পাইয়া ছিল, তাহা সমাজ বিজ্ঞান সম্পর্কে বিন্দুমাত্র ধারণাসম্পন্ন ব্যক্তি ও উপলব্ধি করিতে পারেন।
রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি ও প্রজ্ঞা
রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি ও প্রজ্ঞায় হযরত আবূ বকর (রা)-এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য হযরতের ইন্তেকালের অব্যবহিত পরের একটি ঘটনাই যথেষ্ট। হযরত ইন্তেকাল করিয়াছেন,তাঁহার দাফন-কাফনের কাজ তখনো সম্পূর্ণ হয় নাই। ইতিমধ্যেই মদীনার আনসারগণ ‘সকীফায়ে বনী সায়েদা’য় একত্রিত হইয়া রাসূল পরবর্তী রাষ্ট্রব্যবস্থা ও খিলাফত সম্পর্কে পর্যালোচনা ও চিন্তা-ভাবনা শুরু করিয়া দিয়াছেন। এই আলোচনা ব্যাপদেশে এই প্রশ্নও মাথাচাড়া দিয়া উঠে যে, অতঃপর খিলাফতের অধিকারী কাহারা,আনসারগণ না মুহাজিরগণ?আনসারগণ নিজেদের অধিকার সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন,মুহাজিররাও কিছুমাত্র পশ্চাদপদ ছিলেন না। ফলে এমন একটা পর্যায় আসিল, যখন কেহ কেহ বলিয়া উঠিল*******(আরবী) আমাদের মধ্য হইতে একজন আমীর হইবে আর একজন আমীর হইবে তোমাদের মধ্য হইতে’। পরিস্থিতি এতদূর ঘোলাটে ও উত্তেজনাপূর্ণ হইয়া পড়ে যে, যে কোন মুহূর্তে অসংখ্য শানিত তরবারী কোষমুক্ত হইতে পারিত।
একদিকে এই কঠিন অবস্থা। অপরদিকে হযরত উমর,হযরত আবূ উবাইদাহ (রা)প্রমুখ নেতৃস্থানীয় মুহাজিরগণ মসজিদে নববীতে হযরতের ইন্তেকাল-পরবর্তী পরিস্থিতি সম্পর্কে গভীর আলোচনায় মগ্ন। এ সময় হযরত আবূ বকর (রা) হযরত আলী (রা) সমভিব্যহারে ছিলেন হযরতের কাফন-দাফনের ব্যবস্থাপনায় ব্যতিব্যস্ত। ইতিমধ্যে এক ব্যক্তি সকীফায়ে বনী সায়েদায় আয়োজিত উক্ত সম্মেলনের সংবাদ হযরত উমর ফারুক (রা)-এর নিকট পৌঁছায়। সেই সঙ্গে আনসার নেতৃবৃন্দের বক্তৃতার কথাও তাঁহাকে জানানো হয়। তিনি এই সংবাদ পাইয়া হযরত আবূ বকর (রা)কে বাহিরে ডাকিয়া পাঠাইলেন। হযরত আবূ বকর (রা)নিজের ব্যস্ততা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু যখন তাঁহাকে পরিস্থিতির গুরুত্ত সম্পর্কে অবহিত করা হইল, তখন তিনি স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন যে, অবিলম্বে পরিস্থিতি আয়ত্তাধীন না হইলে উম্মতে মুসলিমা টুকরা টুকরা হইয়া যাওয়ার পূর্ণ আশংকা রহিয়াছে। তিনি ইসলাম ও মুসলিম মিল্লাতের ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া রাসূলের দাফন-কাফনের মত গুরুত্বপূর্ণ কাজ মুলতবী রাখেন। অতঃপর মুসলিম জাতিকে আসন্ন ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করার জন্য চেষ্টা করার উদ্দেশ্য তিনি হযরত উমর ও আবূ উবাইদাহ (রা) সমভিব্যহারে সকীফায়ে বনী সায়েদায় গমন করেন।
সকীফায়ে বনী সায়েদায় পৌঁছিয়া প্রথমে তিনি সমস্ত পরিস্থিতির মূল্যায়ন এবং উহার সঠিক রূপ উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করেন। তিনি স্পষ্টত অনুভব করিতে পারেন যে, কাহারো কাহারো বক্তৃতার তীব্রতায় উপস্থিত লোকদের মন বিশেষভাবে আহত হইয়াছে। অনেকেরই মেজাজ অত্যন্ত খারাপ হইয়া গিয়াছে। এই পরিস্থিতি দর্শনেও তিনি কিছুমাত্র হতাশ হইলেন না। তিনি অবস্থা আয়ত্তে আনিতে ও লোকদের পারস্পরিক ভুল বোঝাবুঝি দূর করিতে লাগিলেন। প্রথম হযরত উমর ফারুক (রা) বক্তৃতা করিতে চাহিলে আবূ বকর সিদ্দীক (রা) তাহাকে বিরত করিলেন।কেননা তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, এই উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতিতে হযরত উমর ফারুক (রা)-এর বক্তৃতা পরিস্থিতিকে অধিকতর ঘোলাটে করিয়া তুলতে পারে। অতঃপর তিনি নিজেই দাঁড়াইয়া বক্তৃতা শুরু করিলেন। তাঁহার এই বক্তৃতা ছিল অত্যন্ত গাম্ভীর্যপূর্ণ,হৃদয়গ্রাহী,মর্মস্পর্শী ও উঁচুমানের ভাষায় অলংকারে সমৃদ্ধ। তাঁহার বক্তব্য ছিল সর্বদিক দিয়া ইনসাফ-ভিত্তিক,বিজ্ঞান ও যুক্তিমূলক। উহা উপস্থিত জনমণ্ডলীর মর্মস্পর্শ করিল, হৃদয় বিগলিত করিয়া দিল। আনসারদের কেহ কেহ এই বক্তৃতার প্রত্যুত্তর দিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু পরিস্থিতি শান্ত রাখার জন্য তাহা কিছুমাত্র সম্ভবপর ছিল না। আনসারদের সম্পর্কে প্রশংসামূলক কথাবার্তা যাহা কিছু বলা সম্ভব ছিল,তিনি তাহা সবই উত্তমরূপে বলিয়াছিলেন এবং সে সঙ্গে বিদ্যমান পরিস্থিতিতে স্বীয় দৃষ্টিকোণও অত্যন্ত অকাট্য যুক্তির ভিত্তিতে পেশ করেন। ফলে সকল কুজ্ঝটিকা,আশংকা ও সংশয়ের সকল গোলক-ধাঁধাঁ নিমেষে বিলীন হইয়া গেল। তিনি যখন দেখিলেন যে, অবস্থা শান্ত হইয়াছে, কলহ-ফাসাদের সকল ঘনঘটা শুন্য মিলাইয়া গিয়াছে, তখন তিনি একজন যোগ্যতম রাষ্ট্রনেতা হিসেবেই প্রস্তাব করিলেনঃ ‘হযরত উমর ও হযরত আবূ উবাইদাহ বিন জাররাহ (রা) তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তিদের অন্যতম, তাঁহাদের মধ্যে যাহার হাতেই ইচ্ছা তোমরা- ‘বায়’আত’ কর’।
হযরত উমর (রা)এই প্রস্তাব শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গে স্বীয় কর্তব্য স্থির করিয়া লইলেন। তিনি অপর কাহারো নাম আলোচ্য বিষয়ে পরিনত হওয়ার পূর্বেই অতীব প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব সহকারে হযরত আবূ বকর (রা)-এর দিকে হাত বাড়াইয়া দিলেন এবং বলিলেনঃ
হস্ত প্রসারিত করুন, আমরা আপনার হস্তেই ‘বায়’আত’ করিব। রাসূলে করীম (স) আপনাকেই নামাযের জন্য তাঁহার স্থলাভিষিক্ত করিয়াছিলেন। এই কারণে মুসলিম সমাজের খলিফা হওয়ার উপযুক্ত ব্যক্তি আপনিই। আমারা আপনার হস্তে ‘বায়’আত’ করিয়া প্রকৃতপক্ষে রাসূলের প্রিয় লোকদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তির হস্তেই ‘বায়’আত’ করার সুযোগ লাভ করিব।
হযরত আবূ উবাইদাহ (রা) সম্মুখে অগ্রসর হইয়া হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-কে সম্বোধন করিয়া বলিলেনঃ
সমগ্র মুজাহিদদের মধ্যে আপনিই উত্তম ব্যক্তি। সাওর-গহবরে আপনিই নবী করীম(স)-এর একক সঙ্গী ছিলেন। মুসলিমদের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ফরয হইতেছে নামায, তাহাতে আপনিই রাসূলে করীম (স)-এর প্রতিনিধি ও স্থলাভিষিক্ত। সুতরাং আপনার বর্তমানে আপনি ব্যতিত খলীফার পদাধিকারী আর কেহই হইতে পারে না।
বস্তুত মুজাহিদদের দুই শীর্ষস্থানীয় নেতা উল্লেখিত ভাষায় নিজেদের মনের কথা ব্যক্ত করায় গোটা মুসলিম উম্মতেরই প্রতিনিধিত্ব করা হইল। তাঁহারা এমন ব্যক্তিকে খলীফা নির্বাচনের প্রস্তাব ও সমর্থন করিলেন, সাম্প্রতিক সমাজে যিনি যথার্থই সর্বাধিক আস্থাভাজন, যোগ্যতাসম্পন্ন ও সর্বোত্তম ব্যক্তি। শেষ পর্যন্ত হযরত আবূ বকর (রা)জাতির গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব গ্রহনে রাযী হইলেন। উপস্থিত জনতা তাঁহার সম্মতি বুঝিতে পারিয়াই তাঁহার হস্তে ‘বায়’আত’ করার জন্য উদ্বেল হইয়া পড়ে। বস্তুতঃ ইসলামের ইতিহাসে ‘সকীফায়ে বনী সায়েদার’ এই সম্মেলন ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ সময় হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা,প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব,বিচক্ষণতা,অবিচল দৃঢ়তা এবং ইস্পাত কঠিন অনমনীয়তা প্রদর্শন না করিলে ইসলামি মিল্লাত তখনি চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইত, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নাই।
বিশ্বনবীর স্থলাভিষিক্ত হওয়ার যোগ্যতা
হযরত আবূ বকর (রা) যাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইলেন, তিনি কোন সাধারণ মানুষ ছিলেন না, তিনি ছিলেন মহান আল্লাহ্ তা’আলার সর্বোচ্চ সম্মানে ভূষিত সর্বশেষ পয়গাম্বর। আল্লাহ্ নিজেই সরাসরি অহী প্রেরণ করিয়া তাঁহাকে পথ-প্রদর্শন করিতেন। ফেরেশতাদের দ্বারা সর্বক্ষণ তাঁহার সাহায্য করিতেন। মু’জিজা দ্বারা তাঁহার প্রতিপত্তি স্থাপন করিতেন। তাঁহার চরিত্র ও যাবতীয় গুনাবলি সরাসরি আল্লাহ্র দীক্ষা ও লালনের প্রভাবে বিকশিত হইয়াছিল। এই জন্য কোন দিক দিয়াই তাঁহার মধ্যে একবিন্দু অসম্পূর্ণতা ও ত্রুটিবিচ্যুতি ছিল না; বরং তিনি ছিলেন সর্বতোভাবে বিকশিত পরিপূর্ণতার সর্বশেষ স্তরে উপনীত মানুষ। এইরূপ মহান ও বিরাট মর্যাদাসম্পন্ন অগ্রনায়কের স্থলাভিষিক্ত হওয়ার দায়িত্ব যথাযথরূপে পালন করা কিছুমাত্র সহজ কাজ নহে। নবীর সার্বিক সৌন্দর্য মাহাত্ন্য বিমুগ্ধ দৃষ্টি পরবর্তী কালের দায়িত্তসম্পন্ন ব্যক্তিকে যত কম মানের তুলাদণ্ডেই ওজন করুক না কেন, তবুও তাহা এতদূর উচ্চ ও উন্নত হইবে যে, সে তুলাদণ্ডে নিজেকে ওজন করার সাহস খুব কম লোকের মধ্যেই হইতে পারে এবং তাহাতে পুরাপুরি উত্তীর্ণ হওয়াও অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। বিশেষতঃএই ওজনকারী লোকেরা নিজেরাই যখন উচ্চ হইতেও উচ্চতর মানদণ্ডে ওজন হইবার যোগ্যতা রাখে, তখন এই কাজটি অধিকতর কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। হযরত আবূ বকর (রা) এইরুপ কঠিন মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হইয়াই মানব জাতির শ্রেষ্টতম পুরুষ ও মহান ব্যক্তিসম্পন্ন অগ্রনেতার স্থলাভিষিক্ত হইয়া ছিলেন এবং নিজের প্রথম নীতিনির্ধারক ভাষণে সুস্পষ্ট ভাষায় এই কথাই বলিয়া দিয়াছিলেন। খলীফা নির্বাচিত হওয়ার অব্যবহিত পরে প্রদত্ত তাঁহার ভাষণের প্রধান অংশ এখানে পেশ করা যাইতেছেঃ
হে জনগণ,আমাকে তোমাদের খলীফা নিযুক্ত করা হইয়াছে, অথচ আমি তোমাদের অপেক্ষা উত্তম ব্যক্তি নহি। কাজেই আমি যদি সঠিক কাজ করি, তাহা হইলে তোমরা আমার সাহায্য ও সহযোগিতা করিও। আর যদি ভুল করি, তবে আমাকে সংশোধন ও সঠিক পথানুসারি করিয়া দিবে।............ তোমাদের মধ্যে প্রতিপত্তিহীন লোক আমার নিকট হইবে প্রতিপত্তিশালী। আমি তাহাদের হক লুণ্ঠনকারীদের নিকট হইতে আদায় করিয়া দিব। পক্ষান্তরে প্রতিপত্তিশালী লোক আমার নিকট হবে প্রতিপত্তিহীন। আমি তাহাদের নিকট হইতে অপরের দ্রব্যাদি (যাহা তাহারা লুণ্ঠন করিয়া লইয়াছে) উসুল করিয়া দিব। .........আমি যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ এবং তাঁহার রাসূলের ফরমাবরদারী করিব, ততক্ষন তোমরাও আমার আনুগত্য করিবে। কিন্তু আমি যদি আল্লাহ্ এবং তাঁহার রাসূলের নাফরমানী করি, তাহা হইলে আমার আনুগত্য করা তোমাদের কর্তব্য নহে।
এই ভাষণে হযরত আবূ বকর (রা)আপন সরকারের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাতে ক্ষমতা প্রয়োগের সীমাও তিনি নির্ধারণ করিয়া দিয়াছেন। এই সীমা সামান্য মাত্র লংঘন করিলে তাঁহার সহিত কিরুপ ব্যবহার করিতে হইবে,তাহা ও নির্দেশিত করেন। সেই সঙ্গে এই মহান সত্যও তিনি উজ্জ্বল করিয়া তোলেন যে, একটি ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান ব্যক্তি হিসাবে রাসূলে করীম (স)-এর প্রদর্শিত পথে চলার জন্য তিনি সর্বতোভাবে দায়ী এবং মুসলিম জনগণ তাঁহার আনুগত্য করিয়া চলিতে ঠিক ততক্ষন পর্যন্ত বাধ্য থাকিবে, যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি নিজে আল্লাহ্র রাসূলের আনুগত্য করিয়া চলিবেন; পরন্তু তিনি ইহার একবিন্দু বরখেলাফ করিলে ইসলামী জনতা শুধু তাঁহার আনুগত্যই অস্বীকার করিতে পারিবে তাহা নহে, তাহার বিরুদ্ধে স্পষ্ট বিদ্রোহ ঘোষণা করাও তাহাদের অধিকার থাকিবে। বস্তুত নবী শ্রেষ্ঠ হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর স্থলাভিষিক্ত হওয়ার দায়িত্ব যথাযথরূপে পালন করা, সেই যুগে হযরতের কথা ও কাজের আলোকে নিজের কথা ও কাজের হিসাব মিলাইবার জন্য সাধারণভাবে সকলকে আহবান জানান সাধারণ ব্যাপার নহে। বিশেষতঃ যাহারা প্রত্যক্ষভাবেই রাসূলে করীম (স)-এর কথা ও কাজ সম্পর্কে পূর্ণরূপে ওয়াকিফহাল এবং যাহাদের মধ্যে কোন বিরাট ব্যক্তিসম্পন্ন লোকেরও সমালোচনা করার দুরন্ত সাহস ও যোগ্যতা পূর্ণ মাত্রায় বর্তমান রহিয়াছে,তাহাদের সম্মুখে উক্তরুপ চ্যালেঞ্জ পেশ করা অত্যন্ত দুঃসাহসের ব্যাপার, সন্দেহ নাই। কিন্তু হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) প্রকৃতই এই দুঃসাহস প্রদর্শন করিয়াছেন এবং তিনি যে বিশ্বনবীর স্থলাভিষিক্ত হওয়ার দায়িত্ব যতখানি পালন করা সম্ভব ততখানিই করিয়াছেন, ইতিহাসই তাহার অকাট্য সাক্ষী। ইহার সত্যতা প্রমাণের জন্য হযরত আবূ বকর (রা)-এর পরবর্তী শ্রেষ্ট মানব হযরত উমর (রা)-এর একটি বাক্য উল্লেখযোগ্য। তিনি তাঁহার (আবূ বকর সিদ্দীকের) অপূর্ব কীর্তিকলাপ দর্শনে মুগ্ধ-বিহম্বল হইয়া অত্যন্ত আফসোস মিশ্রিত কণ্ঠে বলিলেনঃ
ইসলাম ও মুসলমানদের খেদমত করার বাস্তব নমুনা ও মাপকাঠি যদি ইহাই হয় যাহা আপনি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তাহা হইলে আপনার পরবর্তী লোকদের মধ্যে আপনার সমান মর্যাদা অর্জনের হিম্মত কাহারো হইবে না।
হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) যখন খলীফা নিযুক্ত হইলেন, তখন তিনি কোন সুসংগঠিত ও সুসংবদ্ধ রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব লাভ করেন নাই। সত্য কথা এই যে, নবুয়্যাত যুগের পরে স্বয়ং তাহাকেই নূতনভাবে ইসলামী হুকুমতের গোড়া পত্তন করিতে হইয়াছে। এই জন্যই একটি নব-প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের সম্মুখে যত সমস্যা, জটিলতা ও প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হইতে পারে, উহার সবই তাঁহার সম্মুখে পর্বতসমান উঁচু হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এই সব জটিলতার সুষ্ঠু সমাধান করা সকল শাসকের পক্ষে সম্ভব হয় না। তবে আল্লাহ্র নিকট হইতে রাষ্ট্র পরিচালনার বিশেষ যোগ্যতাপ্রাপ্ত লোকেরাই ইহা সঠিকরুপে সম্পন্ন করিতে পারে। প্রথম খলীফা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) স্বভাবতই এইরুপ যোগ্যতার ধারক ছিলেন। এই কারণে বিশ্বনবীর ইন্তেকালের অব্যবহিত পরেই মুসলিম মিল্লাত যে কঠিন সমস্যাবলীর সম্মুখীন হইয়াছিল, হযরত আবূ বকর (রা) তাঁহার অপরিসীম যোগ্যতা-দক্ষতার বদৌলতে উহার সব কিছুরই সুষ্ঠু সমাধান করিয়া লইয়াছিলেন। তিনি অতি অল্প সময়ের মধ্যে যেভাবে ইসলামী রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক পর্যায়ের যাবতীয় হুমকি ও চ্যালেঞ্জের মুকাবিলা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, প্রশাসনিক বিষয়াদিতে যে অপূর্ব দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন,রাষ্ট্রপরিচালনার ইতিহাসে উহার দৃষ্টান্ত নিঃসন্দেহে বিরল। এই প্রসঙ্গে বিস্তারিত বর্ণনা করা এখানে সম্ভব নয়;তবে সংক্ষেপে কয়েকটি বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করা যাইতেছে।
(১) বিশ্বনবীর ইন্তেকালের যে প্রতিক্রিয়া আনসারদের উপর প্রতিফলিত হইয়াছিল এবং হযরত আবূ বকর (রা) যে গভীর বুদ্ধিমত্তা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের দ্বারা সমগ্র প্রতিকূল ও বিশৃঙ্খলা পরিস্থিতি আয়ত্তে আনিয়াছিলেন, ইতিপূর্বে আমরা সে বিষয়ে আলোচনা করিয়াছি। সকিফায়ে বনী সায়েদায় হযরত আবূ বকর (রা)-এর হস্তে খিলাফতের বায়’আত গ্রহণের পর যদিও আনসারদের পক্ষ হইতে কোনরূপ বিদ্রোহাত্মক পদক্ষেপের আশংকা ছিল না; কিন্তু আনসার নেতা সায়াদ-বিন-উবাদার বায়’আত গ্রহণে অস্বীকৃতির পরিণাম মারাত্মক রূপ পরিগ্রহ করিতে পারে বলিয়া মনে করা হইয়াছিল। কোন কোন লোক অনতিবিলম্বে তাঁহার সম্পর্কে নিবর্তনমূলক নীতি গ্রহণেরও পরামর্শ দিয়াছিল। কিন্তু হযরত আবূ বকর (রা) ইহাকে সাময়িক আবেগ-উচ্ছ্বাস মনে করিয়া উপেক্ষা করার নীতিই গ্রহন করেন। তিনি তখনি এই ধারণা করিয়াছিলেন যে, সায়াদের বিরুদ্ধে কোনরূপ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহন করা হইলে সমগ্র আনসার গোত্র বিক্ষুব্ধ হইয়া পড়ার আশংকা রহিয়াছে আর তাহা না করিলে কেবলমাত্র ছায়া ভিন্ন তাহার সঙ্গী আর কেহই হইবে না। হযরত আবূ বকর (রা)-এর এই চিন্তা তখনকার অবস্থায় বাহ্যতঃভুল মনে করা হইয়াছিল; কিন্তু উত্তরকালে অবস্থার গতিধারা প্রমাণ করিয়াছিল যে, হযরত আবূ বকর (রা)-এর মত-ই ছিল নির্ভুল ও সঠিক। উপরন্তু এই অবস্থায় তাঁহার সিদ্ধান্তের বিপরীতে কোন পদক্ষেপ গ্রহন করা হইলে উহার পরিণতি অত্যন্ত মারাত্মক হইত।
(২) আঁ-হযরতের ইন্তেকালের পর নবী করীম (স)-এর পরিবারের মনে হযরত আবূ বকর (রা) এবং তাঁহার হুকুমত সম্পর্কে অনেক ভুল ধারণার সৃষ্টি হইয়াছিল। উহার ফলে বেশ কিছু রাজনৈতিক জটিলতাও মাথাচাড়া দিয়া উঠিয়াছিল। রাসূল পরিবারের লোকদের সহিত মুসলিম জনগণের সম্পর্ক অত্যন্ত নাজুক আবেগময়(emotional) ও সংবেদনশীল(Sensitive)ছিল। হযরত আবূ বকর(রা) ও এই দিক দিয়া কিছুমাত্র পশ্চাদপদ ছিলেন না। কিন্তু এই সব সম্পর্কেরই ঊর্ধ্বে ছিল তাঁহার একটি বিরাট কর্তব্যবোধ, যাহার সংরক্ষণের জন্য তিনি আল্লাহ্ ও জনগণ উভয়ের নিকটই দায়ী ছিলেন। এই দ্বিমুখী ভাবধারার পারস্পরিক দ্বন্দ্বের কারণে হযরত আবূ বকর (রা)-এর যে মানসিক উদ্বেগ প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, উহা তাঁহার তৎকালীন কয়েকটি ভাষণ হইতে সুস্পষ্টরুপে বুঝিতে পারা যায়। তিনি হযরত ফাতিমা (রা), হযরত আলী(রা) ও হযরত আব্বাস (রা)-এর সহিত সাধারণ রাজনৈতিক কলা-কৌশল অবলম্বন করিতে পারিতেন না। কেননা তাহা করা হইল মুসলমানদের আবেগ-উচ্ছ্বাসের সম্পূর্ণ বিপরীত হইত বলিয়া রাজনৈতিক দৃষ্টিতেও অত্যন্ত মারাত্মক আকার ধারণ করিত। আর একজন বিচক্ষণ ও দূরদর্শী ব্যক্তি হিসাবে তিনি নিজেও তাহা কামনা করিতে পারিতেন না। অপর দিকে খিলাফত ইত্যাদির ব্যাপারে তাঁহাদের দৃষ্টিকোণ সমর্থন করাও তাঁহার পক্ষে সম্ভব ছিল না। কেননা তাহা করিলে তিনি শরীয়াতের খেলাফ করিবেন বলিয়াই তাঁহার বিশ্বাস ছিল। সর্বোপরি, রাসূল পরিবারের কোন কোন সদস্য হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর হস্তে তহন পর্যন্ত বায়’আত করেন নাই বলিয়া খিলাফতের মর্যাদা অনেকখানি ব্যাহত হইতেছিল। উপরন্তু এইরূপ পরিস্থিতিতে ইসলামের দুশমনদের পক্ষ হইতে যে কোন মুহূর্তে কঠিন বিপর্যয় সৃষ্টিরও আশংকা একেবারে কম ছিল না। এইসব কিছুই দিবালোকের মত সুস্পষ্ট ছিল;কিন্তু হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) যেমন গণ-আবেগের বিপরীত কিছু করেন নাই, তেমনি শরিয়াতের দৃষ্টিতে যে কর্মনীতি গ্রহন করা উচিত ছিল, তাহাই তিনি অবলম্বন করিয়াছেন। এই দিক দিয়া সর্বাপেক্ষা সান্তনার ব্যাপার এই ছিল যে, এই বিরোধে বনু হাশিম গোত্রের নেতা ছিলেন হযরত আলী(রা) আর তিনি কোন ব্যাপার মতবিরোধ ত করিতে পারেন; কিন্তু তাঁহার দ্বারা কোন প্রকার বিপর্যয় সৃষ্টি যে সম্ভব ছিল না, তাহা ছিল সন্দেহাতীত। ঠিক এই কারণেই হযরত আবূ বকর (রা) অসীম উদার নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন। আর তাঁহার অবলম্বিত নীতিই যে পূর্ণ মাত্রায় বিজ্ঞান-ভিত্তিক ও সত্যাশ্রয়ী ছিল, ইতিহাসই তাহার সাক্ষী।
(৩) হযরত আবূ বকর (রা) যখন খলীফা নিযুক্ত হন, তখন দেশের সার্বিক অবস্থা যারপরনাই খারাপ ছিল। বাহির হইতে রোমকদের আক্রমণের যেমন ভয় ছিল প্রতিটি মুহূর্তে, তেমনি আভ্যন্তরীণ দিক হইতে মক্কা, মদীনা ও তায়েফ ব্যতীত অবশিষ্ট প্রায় সমগ্র আরবে ইসলাম-ত্যাগ ও যাকাত অস্বীকার করার হিড়িক পড়িয়া গিয়াছিল। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন স্থানে মিথ্যা নবুয়্যাতের দাবিদার ও ধন-সম্পত্তির লোভী ব্যক্তিরাও মাথাচাড়া দিয়া উঠে। দেখিতে দেখিতে ইহাদের সমর্থক সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইতে থাকে। অপরদিকে তাবুক ও মূতা’র যুদ্ধ মুসলমান ও রোমকদের মধ্যে এক অন্তহীন সংঘাতের সূচনা করে। রোমকগণ প্রতি মুহূর্তেই মুসলমানদের উপর আক্রমন-উদ্যত হইয়াছিল;মুতা’র যুদ্ধে মুসলমানদের পশ্চাদপসারণের কারণে তাহাদের হিম্মত অধিকতর বৃদ্ধি পায়। এইরূপ অবস্থায় খিলাফতের আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা এবং দেশের প্রধান অঞ্চলসমূহে বিদ্রোহের অগ্নুৎগীরণের সংবাদ প্রচারিত হইলে তাহারা অনতিবিলম্বেই যে মদীনার উপর আক্রমন করিতে পারে, তাহা ছিল এক সাধারণ সত্য কথা। মূলতঃএই দুইটি বিপদ ছিল পূর্ব হইতেই বর্তমান এবং হযরত আবূ বকর (রা)-এর খলীফা নিযুক্তির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে এই উভয় বিপদের সহিত মুকাবিলা করিতে হইয়াছে। এই পরিস্থিতিতেকি অসাধারণ সাহস-হিম্মত ও কি অপূর্ব বুদ্ধি-বিবেচনা সহকারে বিপ দুইটির মুকাবিলা করিয়া তিনি বিপুলভাবে জয়লাভ করেন, তাহা সহজেই উপলব্ধি করা যায়।।
তিনি খলীফা নিযুক্ত হইয়াই সর্বপ্রথম রোমকদের উপর আক্রমণের জন্য প্রস্তুত সৈন্যবাহিনীকে রওয়ানা করাইয়া দিলেন। বস্তুতঃহযরত নবী করীম (স)-এর জীবদ্দশায়ই এই বাহিনীকে হযরত উসামা বিন জায়েদের নেতৃত্বে প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়; কিন্তু হযরতের আকস্মিক রোগাক্রান্ত হইয়া পড়ার কারণে তখনকার মত যাত্রা স্থগিত রাখা হয়। হযরতের ইন্তেকালের পর এই বাহিনী প্রেরণের ব্যাপারে বিপুল সংখ্যক সাহাবী বিপরীত মত পোষণ করিতে শুরু করেন। কেহ কেহ বিদ্যমান আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক দিক দিয়া অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতিতে এইরূপ বাহিনীকে রাজধানীর বাহিরে প্রেরণ করা অদূরদর্শীতার কাজ হইবে বলিয়া যুক্তি প্রদর্শন করে। কাহারও পক্ষ হইতে আবার ক্রীতদাস বংশজাত হযরত উসামার অধিনায়কত্ব সম্পর্কেও আপত্তি উত্থাপন করা হয়। কিন্তু হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) এই সব বাধা-বিপত্তি ও প্রতিকূল পরিস্থিতিতে অবিচলভাবে স্বীয় নীতিতে দণ্ডায়মান রহিলেন। তিনি স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করিলেনঃ ‘যে ঝাণ্ডা রাসূলে করীম নিজে উন্নত করিয়াছেন, আমি তাহা অবনমিত করিতে পারিব না’। তিনি বিরোধী মত পোষণকারীদের প্রস্তাবের জওয়াবে বলিলেনঃ ‘কুকুর ও শৃগালও যদি আমাকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলে,তবুও আমি রাসূলের পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত বাতিল করিতে পারিব না। রাসূল যাহাকে নিযুক্ত করিয়াছেন, আমি তাহাকে কিরূপে পদচ্যুত করিব।
মোটকথা, এইসব বাধা-বিপত্তি ও প্রতিকূল পরিস্থিতি সত্ত্বেও হযরত আবূ বকর (রা) হযরত উসামার নেতৃত্বে সৈন্যবাহিনী রওয়ানা করাইয়াই ছাড়িলেন। বস্তুতঃখলিফাতুল মু’মিনীনের এই অপরিসীম দৃঢ়তা ও মনোবলের ফলেই আল্লাহ্র অসীম রহমত নাজিল হয়। উসামার নেতৃত্বে প্রেরিত সৈন্যবাহিনী বিপুল শান-শওকতপূর্ণ জয়লাভ করিয়া মদীনায় প্রত্যাবর্তন করে। ইহার ফলে আভ্যন্তরীণ দুশমনগণ অত্যন্ত বিস্মিত ও সন্ত্রস্ত হইয়া পড়ে এবং বৈদেশিক শত্রুগণও হইয়া পড়ে অত্যন্ত ভীত ও শঙ্কিত। আরবের বিদ্রোহী গোত্রসমূহ যখনরোমকদের বিরুদ্ধে এই সৈন্য প্রেরণের সংবাদ শুনিতে পাইল, তখন তাহারা মদীনাকেন্দ্রিক রাষ্ট্রের অন্তর্নিহিত বিরাট শক্তির পরিচয় পাইয়া প্রকম্পিত না হইয়া পারিল না।। অপর দিকে হিরাকল স্বীয় রাষ্ট্রের সীমান্ত সংরক্ষণের জন্য অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল।এক কথায়, হযরত আবূ বকর (রা) একই প্রস্তর নিক্ষেপে দুইটি শিকার করিলেন এবং একথা অনস্বীকার্য যে, তাঁহার এই পরিকল্পনা পূর্ণমাত্রায় সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল।
বহিরাক্রমণের বিপদ দূরীভূত হওয়ার পর অবশিষ্ট শক্তি প্রয়োগ করিয়া হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) অত্যন্ত দৃঢ়তা সহকারে আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ-প্রতিবিপ্লব চূর্ণ করিয়া দেন-যদিও সাহাবীদের এক প্রভাবশালী দলের কিছু লোক এই ব্যাপারে উদার নীতি পোষণ করা ও কঠোরতা অবলম্বন না করারই পক্ষে মত পোষণ করিতেন। তাঁহারা বলিতেনঃযাহারা নিজদিগকে মুসলমান বলিয়া পরিচয় দেয়, তাহারা শুধু যাকাত দিতে অস্বীকার করে বলিয়াই তাহাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র প্রয়োগ করা ও জানমালের হেফাজত হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত করা উচিত হইবে না। কিন্তু হযরত আবূ বকর (রা) তাঁহাদের এই দৃষ্টিকোণ কিছুতেই সমর্থন করিতে পারিলেন না। তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলিলেনঃইসলামে নামায ও যাকাত সমপর্যায়ভুক্ত ইবাদত, কাজেই নামায কায়েমের জন্য যদি যুদ্ধ করা যায় তাহা হইলে যাকাত অনাদায়কারীদের বিরুদ্ধে কেন লড়াই করা যাইবে না?তিনি ঘোষণা করিলেনঃ ‘আল্লাহ্র শপথ, যাহারাই নামায ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্যের সৃষ্টি করিবে (নামায পড়িবে ও যাকাত দিবেনা), রাসূলের যুগে যে সব জিনিসের যাকাত দেওয়া হইত তাঁহার একটি রশিও আজ দিতে যাহারা অস্বীকার করিবে,আমি তাহাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করিব। ‘তিনি আরো বলিলেনঃ ‘এই জিহাদে যদি কেহই আমার সঙ্গী না হয়, তবুও আমি একাকীই লড়াই করিব’।
হযরত আবূ বকর (রা)-এর এই নিরাপোষ ও অনমনীয় মনোভাবের ফলেই সমগ্র মুসলমানের হৃদয়ে নবতর কর্মপ্রেরণা ও উদ্দীপনার সৃষ্টি হয় এবং অত্যল্প কালের মধ্যেই খিলাফত-রাজ্য হইতে সকল প্রকার বিদ্রোহ-প্রতি বিপ্লব মূলোৎপাটিত হয়। এই প্রসঙ্গে সর্বাপেক্ষা স্মরণীয় ব্যাপার এই যে, বিদ্রোহের পরিধির অত্যন্ত ব্যাপক আকার ধারণ, মদীনীয় সরকারের চারদিকে বহুবিধ জটিল সমস্যার পরিবেষ্টন এবং সর্বোপরি বিদ্রোহীদের প্রতি বিপুল সংখ্যক আপন লোকদের উদার নীতি অবলম্বনের পক্ষপাতী হওয়া সত্ত্বেও হযরত আবূ বকর (রা) এক বিন্দু দমিত হন নাই, বরং সমঝোতা ও উদার নীতি গ্রহণের সকল প্রস্তাবই তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। কতখানি আত্মবিশ্বাস ও আল্লাহ্র প্রতি নিঃশংক ভরসা থাকিলে এই রূপ সাংঘাতিক পদক্ষেপ গ্রহন করা যাইতে পারে, তাহা সুধীমাত্রেই অনুভব করিতে পারেন।বস্তুত এহেন সংকটপূর্ণ মুহূর্তে হযরত আবূ বকর (রা) যদি এইরূপ অটল মনোভাবের পরিচয় না দিতেন বরং ক্রমবর্ধমান বিদ্রোহ-প্রতিবিপ্লবে ভীত শঙ্কিত হইয়া বিদ্রোহী ও ইসলাম-ত্যাগীদের সম্মুখে অস্ত্র সংবরণ করিতেন, তাহা হইলে ইসলামী রাষ্ট্র-ব্যবস্থার নাম পর্যন্ত ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে মুছিয়া যাইত, তাহাতে একবিন্দু সন্দেহ থাকিতে পারে না। আর তাহাই যদি হইত-তাহা হইলে বিশ্ব-সভ্যতার ইতিহাস আজ সম্পূর্ণ বিপরীতভাবে লিখিত হইত;বরং বিশ্ব-সভ্যতার গতিই স্তদ্ধ হইয়া যাইতে বাধ্য হইত, তাহা সন্দেহাতীত। হযরত আবূ বকর (রা)-এর এই কঠোরভাবে ভূমিকা ও অনমনীয় আদর্শবাদী পদক্ষেপের ফলে ইসলামী সভ্যতায় যে প্রবল জোয়ার আসিয়াছিল, মাত্র সোয়া দুই বৎসরের শাসনকালেই তাহা সমগ্র আরব দেশকে পরিপ্লাবিত করিয়া এবং প্রতিবেশী ইরাক রাজ্যকে পরিসিক্ত করিয়া ও অন্যান্য দেশের উপর হইতে প্রবাহিত হইতে শুরু করিয়াছিল। একটি নবতর সভ্যতার এত আকস্মিক ও সল্পসময়ের মধ্যে এইরূপ ব্যাপকতা,সম্প্রসারণ ও অগ্রগতি লাভের কোন দৃষ্টান্তই বিশ্ব-ইতিহাসে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।
বস্তুতঃহযরত আবূ বকর (রা)-এর নায় মহান চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তি যখন কোন রাষ্ট্রের পরিচালক হয় তখনই সেই রাষ্ট্রের অধিবাসী কোটি জনগণের উন্নতি ও সার্বিক কল্যাণই শুধু নয়, ইসলামেরও সমৃদ্ধি ও প্রতিপত্তি অর্জন সম্ভব হইতে পারে।
হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর খিলাফত
প্রথম খলীফা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর মহান জীবন বহু উজ্জ্বল কীর্তিকলাপে পরিপূর্ণ। বিশেষতঃ তাঁহার সোয়া দুই বৎসরের স্বল্প মিয়াদী খিলাফত আমলে চেষ্টা-সাধনার যে গগনস্পর্শী পিরামিড রচিত হইয়াছে, তাহা কিয়ামত পর্যন্ত অক্ষয় ও অম্লান হইয়া থাকিবে। বিশ্বনবীর ইন্তেকালের অব্যবহিত পরই জাহিলিয়াতের সূচিভেদ্য অন্ধকারে গোটা আরব দেশ-তথা ইসলাম জগত আচ্ছন্ন হইবার উপক্রম হয়। বহু প্রধান ও প্রভাবশালী গোত্র ইসলামী হুকুমতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। নবুয়্যাতের মিথ্যা দাবিদারগণ বিভিন্ন অঞ্চলে বিদ্রোহের পতাকা উড্ডীন করে। যাকাত দিতে অস্বীকারকারীরা শুধু যাকাত দান হইতেই বিরত থাকে নাই, দারুল-খিলাফত মদীনা মুনাওয়ারাকেও লুণ্ঠন করিবার জন্য হুঙ্কার ছাড়ে। এককথায় বলা যায়, ইসলামের প্রচণ্ড মার্তণ্ড অস্তগামী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আকস্মাৎ উহার প্রদীপ্ত দীপশিখা শেষরাত্রের তৈলহীন প্রদীপের ন্যায় নির্বাণোন্মুখ হইয়া পড়ে। কিন্তু রাসূলের স্থলাভিষিক্ত ও মহান খলীফার দূরদৃষ্টি,সাহসিকতাপূর্ণ মনোবল, রাজনৈতিক সূক্ষ্মবুদ্ধি ও অসাধারণ ধৈর্য-স্থৈর্যের ফলে ইসলামের চেরাগ শুধু চির নির্বাণের কবল হইতেই রক্ষা পায় নাই, হেদায়েতের সেই উজ্জ্বল মশাল দ্বারা সমগ্র আরবকে উদ্ভাসিত করিয়া তোলে। এইজন্যই বলিতে হয় যে, বিশ্বনবীর অন্তর্ধানের পর যে মহান ব্যক্তি ইসলামী জীবন ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠাকে ধ্বংসের কবল হইতে রক্ষা করিয়াছেন এবং মুসলিম জাহানের উপর যাহার অপরিশোধ্য ঋণ রহিয়াছে, তিনি হইতেছেন প্রথম খলীফা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)।
দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর ফারুক (রা)-এর খিলাফতকালে অনেক বড় বড় কীর্তি-কাণ্ড সম্পাদিত হইয়াছে, বহুতর কঠিন ও জটিল বিষয়ের সুমীমাংসা হইয়াছে। এমন কি রোমক ও ইরানের বিশাল সাম্রাজ্য পর্যন্ত ইসলামী সয়লাবের আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে। ইহা সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক সত্য, যাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। কিন্তু ইসলামী খিলাফতের বুনিয়াদ সংরক্ষণ, সমগ্র ইসলামী উম্মাহর হৃদয়মনে অপ্রতিরোধ্য বিপ্লব ও আত্মোৎসর্গের প্রচণ্ড ভাবধারার জাগরণ, খিলাফতে ইলাহীয়ার সংগঠন-সংযোজন ও শৃঙ্খলা স্থাপন কাহার দ্বারা সম্ভব হইয়াছে? সর্বোপরি ধ্বংসের ঝঞ্জা-বাত্যা হইতে ইসলামী সমাজ-রাষ্ট্রকে কে বাঁচাইয়াছে?- এইসব প্রশ্নের জওয়াবে কেবলমাত্র আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর নামই উচ্চারণ করা যাইতে পারে। আলোচ্য প্রবন্ধে আমরা আবূ বকর সিদ্দীক (রা) এর খিলাফতকালের কার্যকলাপ ও ইসলামের আকাশস্পর্শী বিস্তারের যাচাই ও পর্যালোচনা উপস্থাপনের চেষ্টা করিব।
খিলাফতের পরামর্শ-ভিত্তিক চরিত্র
একথা অনস্বীকার্য যে, নবুয়্যাতের আদর্শে ইসলামী খিলাফতের প্রথম ভিত্তি স্থাপন করেন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)। প্রথমতঃতাঁহার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় প্রকাশ্য জনমতের ভিত্তিতে। পরন্তু তিনি যতগুলি প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করিয়াছেন,উহার প্রত্যেকটির পশ্চাতেই ইসলামী নাগরিক-জনতার আস্থাভাজন ও স্বাভাবিক প্রতিনিধি মর্যাদাসম্পন্ন শ্রেষ্ট সাহাবিগণকে স্বতঃস্ফূর্ত রায় বর্তমান ছিল। এই জন্য তিনি উপরোক্ত শ্রেণীর সাহাবিগণকে দারুল খিলাফত হইতে দূরে যাইবার অনুমতি দান করেন নাই কখনও। রাসূলে করীম (স) উসামা বাহিনীর সহিত যাইবার জন্য হযরত উমর ফারুক (রা)-এর নাম তালিকাভুক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রথম খলীফা এতদপেক্ষাও অধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য তাঁহাকে মদীনার বাহিরে যাইবার অনুমতি দেন নাই; উসামার নিকট হইতে ইহার অনুমতি তিনি নিজেই গ্রহন করিয়াছিলেন।
সিরিয়া আক্রমণের প্রয়োজন দেখা দিলে বিষয়টিকে তিনি প্রথমে সাহাবাদের বিশিষ্ট জামায়াতের নিকট পরামর্শের জন্য পেশ করেন। বিস্তারিত আলোচনার পর হযরত আলী (রা)-এর একটি প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে জিহাদ-ঘোষণা করার ব্যাপারেও অনুরুপভাবে পরামর্শ গ্রহন করা হয়। অবশ্য একথাও সত্য যে, উমর ফারুক (রা)-এর খিলাফতকালের ন্যায় তখন মজলিসে শুরা সুষ্ঠুরুপে গঠিত ছিলনা; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও কোন জাতীয় রাষ্ট্রীয় ও দ্বীনী গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে বিশিষ্ট সাহাবীদের মত ও রায় গ্রহণে কোন সময়ই অবহেলা করা হয় নাই।
আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা ব্যবস্থা
রাষ্ট্রের স্বরূপ ও ধরণ নির্ধারণের পর দেশের আভ্যন্তরীণ শাসন-শৃঙ্খলা উন্নততর করা এবং গুরুত্বপূর্ণ পদসমূহ বণ্টন ও পদাধিকারীদের সুষ্ঠু নির্বাচন অত্যন্ত জরুরী কাজ। হযরত আবূ বকর (রা)-এর খিলাফতকালে দেশজয় বা রাজ্য বিস্তারের কেবলমাত্র সূচনা হইয়াছিল; কাজেই তাঁহার খিলাফতকে কেবল আরব উপদ্বীপ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ মনে করিতে হইবে। তিনি আরব উপদ্বীপকে কয়েকটি প্রদেশ ও জেলায় বিভক্ত করিয়াছিলেন। মদীনা, মক্কা, তায়েফ, সানয়া,নাজরান, হাযরামওত,বাহরাইন ও দওমাতুল জান্দাল প্রভৃতি স্বতন্ত্র প্রদেশ ছিল। প্রত্যেক প্রদেশেই একজন করিয়া কর্মাধ্যক্ষ(আজিকার ভাষায় গভর্নর) নিযুক্ত ছিলেন।সকল প্রকার রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন তাঁহার কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। দারুল খিলাফতেও প্রত্যেক বিভাগেরই একজন করিয়া প্রধান নিযুক্ত ছিলেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে, হযরত আবূ উবাইদা (রা) সিরিয়ায় সেনাপতি নিযুক্ত হওয়ার পূর্বে অর্থ উজীর পদে অভিষিক্ত ছিলেন, হযরত উমর (রা)ছিলেন বিচারপতি আর হযরত উসমান ও হযরত জায়দ বিন সাবেত (রা) খিলাফত-দরবারের সেক্রেটারি পর্যায়ের কর্মকর্তা ছিলেন।
শাসনকর্তা ও অফিসার নির্বাচনে হযরত আবূ বকর (রা) সব সময়ই নবী করীম (স)-এর যুগের অনুরূপ পদাধিকারী লোকদের প্রাধান্য দিতেন এবং যিনি পূর্বে যে কাজ করিয়াছেন, তাঁহার দ্বারা সেই কাজ লইতে চেষ্টা করিতেন।ফলে তাঁহাকে প্রায় কোন বিভাগেই অযোগ্য ও অনভিজ্ঞ লোক নিয়োগজনিত অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হয় নাই।
হযরত আবূ বকর (রা) একজনকে যখন কোন দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত করিতেন, তখন সাধারণতঃ তাঁহাকে উপস্থিত করিয়া তাঁহার দায়িত্ব ও কর্তব্য বিস্তারিতভাবে বুঝাইয়া দিতেন এবং অত্যন্ত প্রভাবশীল ও মর্মস্পর্শী ভাষায় তাকওয়া,ন্যায়নীতি ও সর্বক্ষেত্রে সুবিচার অবলম্বনের জন্য উপদেশ দান করিতেন। এখানে আমর-বিন আস ও অলীদ বিন আকাবা (রা)-কে যাকাত আদায়কারী নিয়োগকালীন প্রদত্ত উপদেশের অংশ-বিশেষ উল্লেখ করা যাইতেছেঃ
প্রকাশ্যে ও একাকীত্বে আল্লাহ্কে ভয় কর। আল্লাহ্কে যে ভয় করে, আল্লাহ্ তাহার জন্য এমন একটি পথ ও রিযিক লাভের এমন উপায় সৃষ্টি করিয়া দেন,যাহা কাহারও ধারণায় আসিতে পারে না। আল্লাহ্কে যে ভয় করে, আল্লাহ্ তাহার গুনাহ মাফ করিয়া দেন এবং তাহার নেক কাজের ফল দ্বিগুণ ও ততোধিক পরিমাণ দান করেন। জনগণের কল্যাণ কামনা ও খেদমত নিঃসন্দেহে উত্তম তাকওয়ার কাজ।
এমন গুরুত্বপূর্ণ পথে তোমরা অগ্রসর হইতেছ, যেখানে দ্বীনের প্রতিষ্ঠা ও খিলাফতের দৃঢ়তা সাধনের ব্যাপারে বিন্দুমাত্র গাফেলতি বা আতিশয্য ও অবহেলার কোনই অবকাশ নাই। কাজেই অবসাদ ও উপেক্ষার কদর্য অভ্যাস পরিত্যাগ কর।
ইয়াজিদ বিন সুফিয়ানকে সিরিয়ার শাসনকর্তা নিযুক্তির সময় তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেনঃ
হে ইয়াজিদ! তোমার বহু সংখ্যক নিকটাত্মীয় রহিয়াছে;তোমার রাষ্ট্রক্ষমতার দ্বারা তাহাদিগকে অনেক স্বার্থোদ্ধারের সুযোগ করিয়া দিতে পার। কিন্তু জানিয়া লইও, ইহাই আমার সবচেয়ে বড় ভয়। নবী করীম (স) ইরশাদ করিয়াছেনঃ
মুসলমানদের শাসনকর্তা যদি কাহাকেও বিনা অধিকারে শুধুমাত্র প্রীতি হিসাবে মুসলমানদের উপর কর্তৃত্বসম্পন্ন অফিসার নিযুক্ত করে, তবে তাহার উপর আল্লাহ্র অভিশাপ বর্ষিত হয়। আল্লাহ্ তাহার কোন ওযর কিংবা প্রায়শ্চিত্ত কবুল করেন না। এমন কি শেষ পর্যন্ত থাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করিবেন।
শাসকদের প্রতি কড়া দৃষ্টি
সরকারের আইন-কানুন যতই উত্তমভাবে রচিত ও বিধিবদ্ধ হউক না কেন, কিন্তু দায়িত্তসম্পন্ন শাসকদের উপর যদি কড়া দৃষ্টি রাখা না হয় এবং জনগণের তীক্ষ্ণ সমালোচনার সুষ্ঠু ও অবাধ ব্যবস্থা না থাকে, তাহা হইলে গোটা শাসন ব্যবস্থা চূর্ণ-বিচূর্ণ ও কর্তৃপক্ষের প্রতি জনগণের স্বাভাবিক আশা-আকাঙ্ক্ষা ব্যর্থ হইতে বাধ্য। এই কারণেই প্রথম খলীফার স্বাভাবিক বিনয়, নম্রতা, ক্ষমাশীলতা, সহিষ্ণুতা ইত্যাদি মহৎ গুনাবলী থাকা সত্ত্বেও স্থান বিশেষে তাঁহাকে বিশেষ কঠোরতা,পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও তীব্র সমালোচনার মাধ্যমে খাঁটি, ভেজাল ও সদাসদ নির্ণয়ের দুঃসাধ্য কাজ করিতে হইয়াছে। ব্যক্তিগত ব্যাপারসমূহে অতিশয় নম্রতা ও বন্ধুতাবলম্বনই ছিল তাঁহার স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য; কিন্তু সেই সঙ্গে দ্বীনী, প্রশাসনিক ও খিলাফত সংক্রান্ত ব্যাপারে তিনি বিন্দুমাত্র ত্রুতি-অবহেলা বরদাশত করিতেন না। এই কারণে শাসনকর্তাদের মধ্যে যখনি কোন অবাঞ্ছনীয় ত্রুটি পরিলক্ষিত হইত, তখন অত্যন্ত কঠোরতা অবলম্বন করিয়াই তিনি উহার শাস্তি বিধান করিতেন।
দণ্ড বিধানে নম্রতা
হযরত আবূ বকর (রা) ব্যক্তিগতভাবে অপরাধীদের প্রতি অতিশয় নম্র ও সহানুভূতিসূচক ব্যবহার করিতেন। নবী করীম (স)-এর জীবদ্দশায় এক ব্যক্তি ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার কথা তাঁহার নিকট স্বীকার করে। তিনি সহানুভূতিশীল হইয়া তাহাকে তওবা করিতে ও এই অপরাধের কথা বলিয়া না বেড়াইতে উপদেশ দিলেন; কিন্তু অপরাধী শরীয়াতের নির্দিষ্ট দণ্ডবিধান হইতে আত্মরক্ষা করিতে প্রস্তুত না হওয়ায় নবী করীম (স)-এর দরবারে হাযির হইয়া নিজ ইচ্ছায় অপরাধ স্বীকার করিয়া এই দণ্ড গ্রহন করে।
খিলাফতের আমলেও হযরত আবূ বকর (রা)-এর এই প্রকৃতিই বর্তমান ছিল। নবুয়্যাতের মিথ্যা দাবিদার আশয়াস বিন কায়েস গ্রেফতার হইয়া তাঁহাদের দরবারে আসে। শেষ পর্যন্ত সে তওবা করিয়া প্রান ভিক্ষা চায়। হযরত আবূ বকর (রা) তাহাকে কেবল মুক্তিই দান করেন নাই, নিজের সহোদর ভগ্নীর সহিত তাহার বিবাহও সম্পন্ন করেন। বস্তুতঃরাজনৈতিক দৃষ্টিতে খলীফার প্রধান দায়িত্ব হইল জনগণের নৈতিক চরিত্র ও জান-মালের সংরক্ষন। এই দিক দিয়া যদিও তখন পর্যন্ত কোন পুলিশ বিভাগ স্থায়ীভাবে কায়েম ছিল না, তথাপি এই বিভাগটি তখনো নবী করীম (স)-এর স্থাপিত ব্যবস্থা অনুযায়ীই পরিচালিত হইতেছিল। অবশ্য হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা)কে পাহারাদারী ও নিরাপত্তা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিযুক্ত কড়া হইয়াছিল ও কয়েকটি বিশেষ বিশেষ অপরাধের দণ্ডও নির্ধারণ করা হইয়াছিল। এই ব্যাপারে তাঁহাকে ইসলামী পার্লামেন্টের মর্যাদাসম্পন্ন সাহাবা-সম্মেলনে কুরআন হাদীসের ভিত্তিতে পরামর্শ গ্রহন ও ইজতিহাদ করিতে হইয়াছে।
মোটকথা, জনজীবনের শান্তি ও নিরাপত্তা বিধান ও রাজপথসমূহকে সকল প্রকার বিপদ হতে মুক্ত ও নিরাপদ রাখার দিকে প্রথম খলীফা বিশেষ লক্ষ্য আরোপ করিতেন। এই কাজে কেহ বিন্দুমাত্র বাধা ও প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করিলেও তাহাকে কঠোর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিদান করিতেন। কিন্তু কোথাও শরীয়াতের দণ্ড-বিধানের সীমা কখনই লঙ্ঘন করিতেন না।
খিলাফতের অর্থ বিভাগ
নবী করীম (স)-এর যুগে অর্থ বিভাগ পরিচালনার জন্য কোন সুষ্ট ও সুসংগঠিত ব্যবস্থা ছিল না। বিভিন্ন সূত্র হইতে ধন-সম্পদ প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই তিনি উহা অভাবগ্রস্ত জনগণের মধ্যে বণ্টন করিতে দিতেন। হযরত আবূ বকর (রা) এর আমলে এই ব্যবস্থার কোন রদবদল করা হয় নাই। তিনি তাঁহার খিলাফতের প্রথম বৎসরেই মুক্ত ক্রীতদাস, স্ত্রী-পুরুষ এবং উচ্চ-নীচ সকল শ্রেণীর লোকদিগকে মাথাপিছু বিশ দিরহাম দান করিয়াছিলেন। ধন-বণ্টনের ব্যাপারে এইরূপ সমতা রক্ষা সম্পর্কে জনৈক সাহাবী আপত্তি পেশ করিলে তিনি জওয়াবে বলিয়াছিলেনঃ ‘লোকদের মর্যাদা ও গুন-গরিমার মধ্যে পার্থক্য অনস্বীকার্য; কিন্তু ধন-বণ্টনের ব্যাপারে কমবেশী হওয়ার সহিত উহার কি সম্পর্ক থাকিতে পারে?’ তাঁহার খিলাফতের শেষভাগে আনুষ্ঠানিকভাবে একটি ‘বায়তুলমাল’ প্রতিষ্ঠা করা হয়; কিন্তু উহাতে কখনো বিপুল পরিমাণ সম্পদ বা অর্থ সঞ্চিত হতে পারে নাই। ফলে বায়তুলমালের সংরক্ষণ ও পাহারাদারীর কোন ব্যবস্থা গ্রহণেরই প্রয়োজন দেখা দেয় নাই। একবার জনৈক সাহাবী এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেনঃ ‘উহার হেফাজতের জন্য একটি তালা-ই যথেষ্ট’। তাঁহার ইন্তেকালের পর হযরত উমর ফারুক (রা)-এর নেতৃত্বে ‘সানাই’ নামক স্থানে অবস্থিত বায়তুলমাল পরীক্ষা করিয়া দেখা হয় এবং উহাতে মাত্র একটি দিরহাম অবশিষ্ট রহিয়াছে বলিয়া প্রমানিত হয়। ইহা দেখিয়া জনগণ বলিয়া উঠিলঃ ‘আল্লাহ্ আবূ বকরকে রহম করুন’।
সামরিক ব্যবস্থা
নবী করীম (স) –এর আমলে কোন সুসংগঠিত ও সুশৃঙ্খল সৈন্যবাহিনী ছিল না। যুদ্ধের আওয়াজ শ্রুত হইলেই সমগ্র মুসলিম জনতা উহাতে যোগদানের জন্য প্রবল উৎসুক্যের সহিত নবী করীম (স)-এর সম্মুখে সমবেত হইতেন। হযরত আবূ বকর (রা)-এর আমলেও মোটামুটি এই প্রথাই চালু ছিল। অবশ্য তিনি একটি নূতন ব্যবস্থা চালু করিয়াছিলেন। তাহা এই যে, যখন কোন বাহিনী কোন বিশেষ অভিযানে প্রেরণ করিতেন, তখন সমগ্র সৈন্যদিগকে নান উপ-বাহিনীতে বিভক্ত করিয়া উহার প্রতিটির জন্য এক একজন সেনাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিয়া দিতেন। এইভাবে আমীরুল উমারা বা ‘কমান্ডার-ইন চীফ’ নিয়োগের প্রথাও প্রথম খলীফার আমলেই সূচিত হইয়াছিল এবং হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদই সর্বপ্রথম এই গুরুত্বপূর্ণ ও অত্যধিক সম্মানিত পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।
বস্তুতঃ সৈন্যবাহিনীকে এইভাবে সুসংবদ্ধ ও সন্নিবেশিত করার ফলে মুসলিম মুজাহিদীনের পক্ষে রোমকদের সুসংবদ্ধ সৈন্যবাহিনীর মুকাবিলা করা অতিশয় সহজ হইয়াছিল।
সৈনিকদের চরিত্রগঠন ও প্রশিক্ষন ব্যবস্থা
নবী করীম (স) ও খিলাফতে রাশেদার আমলে সংঘটিত প্রতিটি যুদ্ধ-সংগ্রাম আল্লাহ্র সন্তোষ বিধান ও ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষার উদ্দেশ্যই চালিত হইয়াছে। এই কারণে এই উদ্দেশ্য আত্মোৎসর্গীকৃত জনতার নৈতিক চরিত্রের উন্নতি বিধানের দিকে তখন বিশেষ গুরুত্ত সহকারে দৃষ্টি দেওয়া হইত। ফলে ইসলামী বাহিনী নৈতিক চরিত্রের দিক দিয়া সমগ্র বিশ্বের শ্রেষ্টত্তের অধিকারী হইয়াছিল। নবী করীম (স)-এর পরে হযরত আবূ বকর (রা) ও সামরিক প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে এই দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াছেন। বিশেষ বিশেষ অভিযানে সৈন্যবাহিনী প্রেরণের সময় তিনি সেনাধ্যক্ষর সহিত বহুদূর অগ্রসর হইয়া যাইতেন ও মূল্যবান উপদেশ দান করিয়া তাহাকে বিদায় দিতেন। সিরিয়া অভিযানে প্রেরণের সময় সেনাধ্যক্ষর নিম্নোক্তরুপে উপদেশ দিয়াছিলেনঃ
তোমার এমন লোকদের সাক্ষাত পাইবে, যাহারা আল্লাহ্র উপাসনায় আত্মনিয়োগ করিয়া রহিয়াছেন। তাহাদের উপর আক্রমন করিবে না। এতদ্ব্যতীত আরও দশটি উপদেশ তোমাদিগকে দিতেছিঃ কোন স্ত্রী, শিশু ও বৃদ্ধ লোককে হত্যা করিবে না, ফলবান গাছ কর্তন করিবে না, কোন জনপদ বা আবাদ স্থানকে জনশূন্য করিবে না। ছাগল ও উষ্ট্র খাদ্য-প্রয়োজন ব্যতীত কখনো জবেহ করিবে না। খেজুর বাগানে অগ্নিসংযোগ করিবে না। গণিমতের মাল কোনরূপ অপহরণ করিবে না এবং কাপুরুষ ও সাহসহীন হইবে না।
যুদ্ধের সরঞ্জাম সংগ্রহ
হযরত আবূ বকর (রা) যুদ্ধের সরঞ্জাম সংগ্রহের জন্য একটি নির্দিষ্ট পরিকল্পনা কার্যকর করিয়াছিলেন। বিভিন্ন সূত্রে সরকারী ফান্ডে যাহা কিছু জমা হইত, উহা হইতে একটি মূল্যবান অংশ তিনি পরিবহন ও অস্ত্র ক্রয়ের কাজে ব্যয় করিতেন। কুরআন মজীদে গণিমতের মালে আল্লাহ্, রাসূল ও নিকটাত্মীয়দের জন্য যে অংশ নির্দিষ্ট করা হইয়াছে, তাহা সবই এই সামরিক প্রয়োজন পূরণের খাতে ব্যয় করা হইত। নবী করীম (স) অন্যান্য জরুরী কাজের পর এই খাতেই অবশিষ্ট সম্পদ ব্যয় করিতেন।
উষ্ট্র ও অশ্ব পালনের প্রথম খলীফা ‘বকী’ নামক স্থানে একটি বিশেষ চারণভূমি নির্দিষ্ট করিয়াছিলেন। এখানে হাজার হাজার সরকারী জন্তু প্রতিপালনের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। সদকা ও যাকাত বাবদ আদায়কৃত সরকারী জন্তু এখানেই রাখা হইত।
সামরিক কেন্দ্রসমূহ পর্যবেক্ষণ
হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) বার্ধক্যজনিত দুর্বলতার ফলে নানা দুশ্চিন্তা ও মনোবেদনায় ভারাক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও নিজেই সামরিক ছাউনীসমূহ পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ করিতেন এবং সৈনিকদের মধ্যে বাস্তব ও আধ্যাত্মিকতার দিক দিয়া কোন ত্রুটি –বিচ্যুতি দেখিতে পাইলে সঙ্গে সঙ্গে উহার সংশোধনও করিয়া দিতেন। কোন একটি বিশেষ অভিযান উপলক্ষে ‘জরফ’ নামক স্থানে বিপুল সংখ্যক সৈন্য সমাবেশ করা হয়। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) উহা পরিদর্শন করিতে গেলেন। তিনি ‘বানুফজারাহ’ নামক স্থানে অবস্থিত তাঁবুতে উপস্থিত হইতে মুজাহিদগণ দাঁড়াইয়া তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিল। এখানে তিনি বিভিন্ন গোত্র হইতে আগত সৈনিকদের মধ্যে পারস্পরিক আভিজাত্য ও শ্রেষ্টত্তের গৌরববোধ লক্ষ্য করিলেন। তিনি উপদেশের সাহায্যে বংশীয় ও গোত্রীয় আভিজাত্য এবং পারস্পরিক হিংসা-দ্বেষ অবদমিত করিয়া সকলের মধ্যে ইসলামী সহনশীলতা ও ভ্রাতৃত্ববোধ জাগাইবার জন্য চেষ্টা করিলেন।
অনৈসলামী প্রথার প্রতিরোধ
নবীদের প্রচারিত ধর্মমত ও জীবন ব্যবস্থার উত্তরকালে বিকৃত হইয়া যাওয়ার মূলে সবচেয়ে বড় কারণ হইল লোকদের মধ্যে ক্রমশঃ বিদয়াতের প্রচলন ও প্রশ্রয় লাভ। ইহার ফলে, বিদয়াতী ব্যবস্থাসমূহই মূল ধর্মের স্থান লাভ করে ও আসল ধর্ম বিলুপ্ত হয়। হযরত আবূ বকর (রা)-এর আমলে ইসলামী সমাজে বিদয়াতের কোন বিশেষ সূচনা পরিলক্ষিত হয় নাই। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও কখনও এবং কোথাও তেমন কিছু দেখা গেলেই তিনি অনতিবিলম্বে উহা দূর করিতে চেষ্টিত হইতেন।
কুরআন ও হাদীস সম্পর্কে হযরত আবূ বকর (রা)-এর ভূমিকা
নবুয়্যাতের মিথ্যা দাবিদারদের সহিত সংঘটিত লড়াইসমূহে বহুসংখ্যক হাফিজে কুরআন মুজাহিদ শহীদ হন। বিশেষতঃইয়ামামার রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে এত বেশিসংখ্যক হাফিজে কুরআন শাহাদত বরণ করেন যে, তাহাতে দায়িত্তসম্পন্ন সাহাবীদের মনে কুরআন মজীদের বিলুপ্ত হইয়া যাওয়ার আশংকা দেখা দেয়। এই জন্য অবিলম্বে কুরআন মজীদ সংগ্রহ, প্রণয়ন ও সন্নিবেশিত করার প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে দেখা দেয়।
বস্তুতঃকুরআন মজীদের আয়াত ও সূরাসমূহ বিশেষ বিশেষ সময়ে ও বিশেষ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নাজিল হইয়াছে এবং নবী করীম (স)-এর নির্দেশে তাহা সঙ্গে সঙ্গেই নির্দিষ্ট সাহাবীদের দ্বারা লিখিত হইয়াছে। খর্জুর পত্র, উষ্ট্রের চামড়া, অস্থি, পাথর ও কাষ্ঠের উপরই তাহা সুস্পষ্টরুপে লিখিত ছিল। হযরত আবূ বকর (রা)-এর নির্দেশে তাহা একত্রে সন্নিবেশিত করা হয় ও একখানা সুসংবদ্ধ গ্রন্থের রূপ দান করা হয়। ইসলামী দৃষ্টিতে ইহা যে কত বড় কীর্তি ছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়।
হাদীস সম্পর্কে হযরত আবূ বকর (রা)-এর ভূমিকা ছিল অত্যন্ত সতর্কতাপূর্ণ। তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন যে, কোন হাদীসের সত্যতা সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাসী ও সর্ব প্রকারের সন্দেহ বিমুক্ত না হইয়া উহা রেওয়ায়েত করা ঠিক নহে। তিন নিজে কখনো কোন হাদীসকে উহার একাধিক সমর্থক ও সাক্ষী না পাইলে গ্রহন করিতেন না।
ইসলামী আইন বিভাগ স্থাপন
ইসলামী আইন সম্পর্কে গবেষণা, অনুসন্ধান ও বিচার-বিশ্লেষণের গুরুত্বপূর্ণ কার্য সম্পাদনের জন্য হযরত আবূ বকর (রা) একটি বিশেষ বিভাগ স্থাপন করেন। হযরত উমর, হযরত উসমান, হযরত আলী, হযরত আবদুর রাহমান বিন আউফ, হযরত মুয়াজ বিন জাবাল, হযরত উবাই বিন কায়াব, হযরত জায়েদ বিন সাবেত (রা) প্রমুখ শ্রেষ্ঠ মনিষী ও চিন্তাবিদগণ এই কাজে নিযুক্ত ছিলেন। জনগণের জিজ্ঞাসিত ফতোয়ার জওয়াব দান করাও ইঁহাদেরই দায়িত্ব ছিল।
ইসলাম প্রচার
রাসূলের প্রতিনিধি মর্যাদাসম্পন্ন খলীফার অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ছিল ইসলামী আদর্শ প্রচার। এই দিকে হযরত আবূ বকর (রা)-এর প্রথম হইতেই বিশেষ লক্ষ্য ও দৃষ্টি ছিল। বস্তুতঃইসলামী আকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্রসমূহ ছিল সত্যের জন্য আত্মোৎসর্গীকৃতপ্রাণ হযরত আবূ বকর (রা)-এর আপ্রান প্রচেষ্টার ফসল। কিন্তু খিলাফতের গুরুভার অর্পিত হওয়ার পর স্বাভাবিকভাবেই এইদিকে তাঁহার অধিক প্রবণতা ও তৎপরতা দেখা দেয়। ফলে সমস্ত আরবদেশ ইসলাম প্রচারের বলিষ্ঠ ধ্বনিতে মুখরিত হইয়া উঠে। চতুর্দিকে প্রেরিত মুজাহিদদিগকে ইসলাম প্রচারের জন্য হযরত আবূ বকর (রা) নির্দেশ দিলেন। বিভিন্ন অঞ্চলে বিক্ষিপ্ত আরব গোত্রসমূহে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছাইবার জন্য তিনি বিশেষ প্রতিনিধি দল প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা পূর্ণ একাগ্রতা ও ঐকান্তিক নিষ্ঠা সহকারে এই কাজ সম্পন্ন করিতেন। ইহার ফলে দূর-নিকটের সকল মূর্তিপূজক ও খৃষ্টান ধর্মাবলম্বী ইসলামে দীক্ষিত হয়। হযরত খালেদ (রা)-এর ইসলামী দাওয়াতে সাড়া দেয় ইরাক, আরব ও সিরীয় সীমান্তবর্তী আরব গোত্রসমূহ।
নবী করীম (স)-এর ওয়াদাসমূহ পরিপূরণ
নবী করীম (স)-এর আমলের ঋণসমূহ পরিশোধ করা ও প্রদত্ত ওয়াদা-প্রতিশ্রুতিসমূহ যথাযথভাবে পালন করাও খিলাফতের অন্যতম দায়িত্ব ছিল। হযরত আবূ বকর (রা) প্রথম অবসরেই এ কাজগুলি সম্পন্ন করেন। বিশেষতঃ ‘বাহরাইন’ বিজয়ের ফলে বিপুল ধনসম্পদ হস্তগত হইলে পর তিনি সাধারণভাবে ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, নবী করীম (স)-এর নিকট কাহারো পাওনা থাকিলে কিংবা তাঁহার কোন ওয়াদা অপূর্ণ থাকিলে আমার নিকট হইতে তাহা পূরণ করা যাইতে পারে।
নবী করীম (স)-এর পরিবারবর্গ ও আত্মীয়দের সহিত ব্যবহার
নবী করীম (স)-এর পরিবারবর্গ ও নিকটাত্মীয়দের সহিত ‘ফিদাকের’ বাগানকে কেন্দ্র করিয়া প্রথমে তাঁহার সহিত কিছুটা ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হইলেও তিনি তাঁহাদের সহিত সকল সময় অত্যন্ত হৃদ্যতা,সহানুভূতি, ও শ্রদ্ধাপূর্ণ ব্যবহার করিয়াছেন। উম্মাহাতুল মু’মিনীনের সুখ-শান্তি বিধান ও তাঁহাদের যাবতীয় প্রয়োজন পূরণের দিকে তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য লোকদের সম্পর্কে রাসূলে করীম (স) যেসব অসীয়ত করিয়া গিয়াছেন, তিনি পূর্ণ সম্মান ও ভক্তিসহকারে সেইগুলি পূরণ করিয়াছেন।
যিম্মি প্রজাদের অধিকার রক্ষা
নবুয়্যাতের যুগে ইসলাম রাষ্ট্রে যে সব বিধর্মীদের আশ্রয়দান করা এবং লিখিত চুক্তিনামার মাধ্যমে যাহাদের সহিত বিশেষ সন্ধি করা হইয়াছিল, হযরত আবূ বকর (রা) তাহাদের যাবতীয় অধিকার যথাযথরূপে রক্ষা করিয়াছেন। অনুরুপভাবে তাঁহার খিলাফত আমলে বিজিত দেশসমূহে অমুসলিম যিম্মী প্রজাদের তিনি মুসলিম প্রজাদের প্রায় সমান অধিকার দান করিয়াছিলেন। ‘হীরা’র খৃষ্টান অধিবাসীদের সহিত যে চুক্তি-নামা স্বাক্ষরিত হইয়াছিল, তাহা নিম্নরুপঃ
তাহাদের খানকাহ ও গীর্জাসমূহ ধ্বংস করা হইবে না, প্রয়োজনের সময়ে আশ্রয় গ্রহণের উদ্দেশ্যে নির্মিত কোন প্রাসাদও চূর্ণ করা হইবে না। ঘণ্টা বাজানো ও শিঙ্গা ফুকাইতে বাধা দেওয়া হইবে না। তাহাদের বিশেষ উৎসব অনুষ্ঠানের সময়ে ক্রুশ মিছিল বাহির করিতে নিষেধ করা হইবে না।
দীর্ঘ চুক্তিনামা হইতে এখানে মাত্র কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করা হইল। ইহা হইতে ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় পরধর্ম-সহিষ্ণুতার উজ্জ্বল নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়।
প্রথম খলীফার আমলে জিজিয়া ও সাধারণ করের পরিমাণ ছিল অত্যন্ত কম। উপরন্তু তাহা কেবল সামর্থ্যবান লোকদের উপর ধার্য করা হইত। ‘হীরা’ অঞ্চলের সাত সহস্র অধিবাসীর মধ্যে এক সহস্র অধিবাসীকেই সকল প্রকার জিজিয়া কর হইতে নিষ্কৃতি দেওয়া হইয়াছিল আর অবশিষ্ট লোকদের উপরও মাথাপিছু বার্ষিক মাত্র দশ দিরহাম কর ধার্য করা হইয়াছিল। উল্লেখিত চুক্তিতে ইহারও উল্লেখ ছিল যে, কোন যিম্মী বৃদ্ধ, অক্ষম ও দরিদ্র হইয়া গেলে তাহার নিকট হইতে কোন করই গ্রহন করা হইবে না; উপরন্তু বায়তুলমাল হইতে তাহার ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করা হইবে। দুনিয়ার ইতিহাসে এইরূপ অপক্ষপাত প্রজাপালন ও উদার আচরণের কোন দৃষ্টান্ত খুঁজিয়া পাওয়া যায় কি?
উমর ফারুক (রা)-এর চরিত্র বৈশিষ্ট্য
বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (স) স্বীয় জীবনের অকৃত্রিম সাধনার ফলে এক পূর্ণাঙ্গ আদর্শবাদী ও উন্নত চরিত্রবিশিষ্ট সমাজ গঠন করিয়াছিলেন। তাঁহার গঠিত সমাজের প্রতিটি ব্যক্তিই আদর্শবাদী ও নৈতিক চরিত্রের দিক দিয়া ছিল পর্বত-শৃংগের মত উন্নত, অন্যায় ও বাতিলের সম্মুখে অনমনীয় এবং বিরুদ্ধবাদীদের দৃষ্টিতে অত্যন্ত দুর্জয় ও দুর্ভেদ্য। প্রায় সকল সাহাবী সম্পর্কেই এই কথা পূর্ণ মাত্রায় সত্য ও প্রযোজ্য। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ইহা অনস্বীকার্য যে কোমলতা, কঠোরতা, বিনয়,নম্রতা এবং সহিষ্ণুতার দিক দিয়া তাঁহাদের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান ছিল। এই পার্থক্য স্বভাবগত তারতম্যের কারণে এক বাস্তব সত্যরূপে স্বীকৃত। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা যখন হযরত উমর ফারুক (রা)-এর ব্যক্তি চরিত্র পর্যালোচনা করি, তখন আমাদের সম্মুখে এক অসাধারণ লৌহ-মানবের বিস্ময়কর ভাবমূর্তি সমুদ্ভাসিত হইয়া উঠে। বস্তুত হযরত উমর (রা) ইসলামী সমাজে এক অপরিসীম বীর্যবান, তেজোময়, নির্ভীক ও অনমনীয় ব্যক্তিত্তের অত্যুজ্জ্বল আদর্শ সংস্থাপন করিয়াছেন। ইসলামী খিলাফতের বিশাল আকাশে তিনি এক দেদীপ্যমান চন্দ্রের সমতুল্য। খিলাফতের ময়দানে তাঁহার ভূমিকা অত্যন্ত বলিষ্ঠ ও সমুন্নত।
উমর চরিত্রের এই বলিষ্ঠতা তাঁহার জীবনের প্রথমকাল হইতেই পরিলক্ষিত হয়। ইসলাম-পূর্ব যুগের সমাজে তিনি এক অসামান্য বীর-পুরুষ রুপেই পরিচিত ছিলেন। তিনি যখন সাতাইশ বৎসরের এক উদীয়মান বীর যুবক, ঠিক তখনি আরবের মরুবক্ষে ইসলাম-সূর্যের অভ্যুদয় ঘটে। মক্কার পর্বতচূড়া হইতে দিক প্রকম্পক তওহীদ বানী ধ্বনিত হয়। উমর ফারুকের নিকট এই ধ্বনি ছিল সম্পূর্ণ অভিনব ও অপরিচিত। তিনি ইহা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ও বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠেন। ফলে যাহার সম্পর্কেই তিনি ইসলাম কবুল করার খবর পাইতেন, তিনি তাহারই প্রচণ্ড শত্রু হইয়া দাঁড়াইতেন। তাঁহার বংশেরই একটি ক্রীতদাসী ইসলাম কবুল করিলে তাহাকে তিনি অবিশ্বাস্য রকমে প্রহার করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত আর যাহার সম্পর্কেই তিনি ইসলাম কবুল করার সংবাদ পাইতেন, তাঁহাকেই তিনি নাস্তানাবুদ করার জন্য দৃপ্ত পদক্ষেপে অগ্রসর হইতেন। কিন্তু বড়ই আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, এত আঘাত করিয়াও তিনি একটি মাত্র লোককেও ইসলাম ত্যাগে প্রস্তুত করিতে পারনে নাই। শেষ পর্যন্ত তিনি স্বয়ং বিশ্বনবীকেই খতম করার সিদ্ধান্ত গ্রহন করেন। একদা তীক্ষ্ণ শানিত কৃপাণ স্কন্ধে ঝুলাইয়া দৃপ্ত পদক্ষেপে তিনি সেই উদ্দেশ্যেই যাত্রা করিলেন। কিন্তু পথিমধ্যে যখনি তিনি শুনিতে পাইলেন যে, তাঁহারই আপন ভগ্নি ও ভগ্নিপতি ইসলাম কবুল করিয়াছেন, তখন তাঁহার উপর যেন বজ্রপাত হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া গিয়া ভগ্নী ও ভগ্নীপতিকে এতই প্রহার করেন যে, তাঁহাদের দেহ হইতে রক্তের অবরল ধারা প্রবাহিত হইতে শুরু করে। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও তাঁহাদের দিলে ইসলামের প্রতি ঈমানের একবিন্দু দুর্বলতা দেখা দেয় নাই। উপরন্তু তাঁহারা উমর ফারুককে সম্বোধন করিয়া বলিলেনঃ “তোমার মনে যাহা আসে কর। কিন্তু আমাদের দিল হইতে ইসলামের প্রতি ঈমানের অত্যুজ্জ্বল দীপমশাল নির্বাপিত করা তোমার সাধ্যাতীত”।
নওমুসলিমদের এই অনমনীয়তা দর্শনে উমর ফারুক (রা) বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়েন। কি কারণে ইহারা ইসলামের জন্য এতদূর আত্মহারা ও উৎসর্গীকৃতপ্রাণ হয় এবং কোন পরশপাথরের ছোঁয়ায় একজন অসভ্য নাফরমান লোক মানুষ পদবাচ্য হইয়া উঠে তাহা ভাবিয়া তিনি দিশাহারা হইয়া যান। শেষ পর্যন্ত তিনিও ইসলামের সুদৃঢ় নীতি-দর্শনের সম্মুখে মস্তক অবনত করিতে বাধ্য হন। তাঁহার ন্যায় একজন অসামান্য বীর-পুরুষের ইসলাম গ্রহণে তদানীন্তন আরবের দুই পরস্পর বিরোধ সমাজেই দারুণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। কাফির সমাজ যেমন আশ্চার্যািন্বত হয় তেমনি হয় হতাশাগ্রস্ত; পক্ষান্তরে ক্ষুদ্র পরিসরের ইসলামী সমাজে উৎসাহ উদ্দীপনার এক যৌবন জোয়ার পরিলক্ষিত হয়, তখন মুসলমানরা ছিলেন অতিশয় দুর্বল, শক্তিহীন ও অসহায়। প্রকাশ্যভাবে ইসলামী জিন্দেগী যাপন ও জরুরী অনুষ্ঠানাদি পালন তো দূরের কথা, নিজদিগকে মুসলিমরূপে ব্যক্ত করাও তাঁহাদের পক্ষে কঠিন বিপদের কারণ হইয়া পড়িয়াছিল। বিশেষতঃতাহাদের পক্ষে আল্লাহ্র ঘরে আল্লাহ্র বন্দেগী করা তো ছিল একেবারে অসম্ভব। হযরত উমর (রা)-এর ন্যায় নির্ভীক বীর পুরুষের ইসলাম গ্রহণে সহসা অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। তিনি নিজেই মুসলিম হওয়ার কথা রাষ্ট্র করিয়া দিলে কাফির সমাজ তাঁহার প্রতি অত্যন্ত বিরুপ ও ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে। তাঁহার মামা প্রভাবশালী কাফির নেতা আস বিন ওয়ায়েল তাঁহাকে আশ্রয় দিতে চাহিলে তিনি তাঁহার স্বভাবসুলভ তেজস্বীতা ও বীর্যবত্তার দরুণ তাহার আশ্রয় গ্রহন করিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। কেননা ইসলামের বিপ্লবী কালেমা ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু’র উপর বিশ্বাস স্থাপনের পর কোন কাফির ব্যক্তি বা শক্তির আশ্রয় গ্রহন করা, কোন আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে মোটেই শোভন ব্যাপার নহে। উপরন্তু তিনি মুসলিমদের সমভিব্যহারে কা’বা ঘরে গিয়াই নামায আদায় করেন। মূলত বীর উমরের সাহসিকতার বলেই এই কাজটি সম্ভব হইয়াছিল। এইজন্য নবুয়্যাতের দরবারে তিনি ফারুক (হক ও বাতিলের পার্থক্যকারী) উপাধিতে ভূষিত হন।
হযরত উমর (রা) ইসলাম গ্রহণের পর হিজরাত পর্যন্ত মক্কা শরীফে প্রায় ছয়-সাত বৎসরকাল অবস্থান করেন। এই সময় কাফিরদের তরফ হইতে মুসলিমদের উপর যে অমানুষিক অত্যাচার ও জুলুম-নিষ্পেষণ সংগঠিত হয়, অন্যান্যদের সঙ্গে হযরত উমর (রা) ও তাহা অবলীলাক্রমে সহ্য করিয়াছেন। বস্তুত ইসলামের জন্য অতুলনীয় আত্মোৎসর্গিতা,অপূর্ব নৈতিক দৃঢ়তা ও চারিত্রিক অনমনীয়তা না থাকিলে কাফিরদের পৈশাচিক নির্যাতনের যাতাকলে নিষ্পিষ্ট হইয়াও ঈমানকে বাঁচাইয়া রাখা তদানীন্তন মুসলিমদের পক্ষে বড়ই কঠিন ব্যাপার ছিল।
ইসলামের প্রথম যুদ্ধ বদরের ময়দানে সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে হযরত উমর (রা)যে সূক্ষ্ম বিচার-বুদ্ধি,আত্মোৎসর্গী ভাবধারা ও অনমনীয় দৃঢ়তা প্রদর্শন করেন, ইসলামের ইতিহাসে তাহা উজ্জ্বল অক্ষরে লিখিত। ইসলামের জন্য তিনি অতি বড় নিকটাত্মীয়কেও একবিন্দু ক্ষমা করিতে প্রস্তুত হন নাই। যুদ্ধের ময়দানে তাঁহার মামা ‘আস তাঁহার নিজ তরবারীর আঘাতেই নিহত হয়। এই পরম আত্মীয়ের বক্ষে অস্ত্র বিদ্ধ করিতেও তিনি কিছু মাত্র কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। ইসলামের জন্য এই আত্মত্যাগ বস্তুতঃই তুলনাহীন।
বদর যুদ্ধে মুসলিমরা গৌরবোজ্জ্বল বিজয় অর্জন করে এবং ইহাতে কম-বেশী সত্তর জন কাফির সরদার মুসলিমদের হস্তে বন্দি হয়। ইহাদের সহিত কিরুপ ব্যবহার করা হইবে, তাহা লইয়া আলোচনা শুরু হইলে হযরত উমর ফারুক (রা) স্পষ্ট অভিমত প্রকাশ করিয়া বলিলেনঃ “ইহাদের হত্যা করাই বাঞ্ছনীয় এবং আমাদের মধ্যে প্রত্যেকেরই নিজ নিজ আত্মীয়কে নিজ হস্তে যবেহ করা কর্তব্য”।
ষষ্ট হিজরী সনে চৌদ্দ শত মুসলিম সমভিব্যাহারে নবী করীম (স) হজ্জের উদ্দেশ্যে মক্কা যাত্রা করেন। যুলহুলায়ফা নামক স্থানে পৌঁছিয়া তিনি জানিতে পারেন যে, মক্কার কুরাইশগন এই বৎসর মুসলিমদিগকে কিছুতেই নগরীতে প্রবেশ করিতে দিবে না। এই পরিস্থিতিতে হযরত উসমান (রা) কে শহীদ করিয়া ফেলার সংবাদ ছড়াইয়া পড়ে। এই সময় নবী করীম (স) সাহাবীদের নিকট হইতে আত্মোৎসর্গের ‘বায়’আত’ গ্রহন করেন। হযরত উমর (রা) ইহাতে অগ্রবর্তী ছিলেন। শেষ পর্যন্ত কুরাইশদের সহিত সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরিত হইলে উহার একটি শর্ত উমর ফারুক (রা)-এর নিকট সুস্পষ্টরূপে অগ্রহণযোগ্য মনে হয় এবং তাঁহার প্রখর আত্মসম্মানবোধ সাহসিক প্রকৃতিতে প্রচণ্ড আঘাত হানে। তিনি অনতি-বিলম্বে রাসূলের দরবারে উপস্থিত হইয়া আরজ করিলেনঃ “আমরা যখন বাস্তবিকই সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, তখন বাতিলের সহিত এত নম্র ও নত হইয়া সন্ধি করার প্রয়োজন কি?”
মক্কা বিজয়ের বৎসরই হুনাইন যুদ্ধ সংঘটিত হয়। হযরত উমর (রা) এই যুদ্ধে অত্যন্ত দৃঢ়তা সহকারে লড়াই করেন। নবম হিজরীতে যখন রোমান সম্রাটের মদীনা আক্রমণের সংবাদ ছড়াইয়া পড়ে, তখন নবী করীম (স)-এর আবেদনক্রমে হযরত উমর ফারুক (রা) তাঁহার মোট সম্পত্তির অর্ধেক আনিয়া রাসূলের খেদমতে পেশ করেন।
বিশ্বনবীর ইন্তেকালের সংবাদ পাইয়া গোটা মুসলিম সমাজ প্রচণ্ড মর্ম জ্বালায় ভাঙ্গিয়া পড়ার উপক্রম হয়। এদিকে কুটিল চরিত্রের মুনাফিকগন সুযোগ বুঝিয়া কোন মারাত্মক বিপর্যয় সৃষ্টির জন্য চেষ্টিত হইতে পারে মনে করিয়া হযরত উমর ফারুক (রা) মসজিদে নববীতে দাঁড়াইয়া ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা করিতে শুরু করেনঃ “যে বলিবে বিশনবী ইন্তেকাল করিয়াছেন, তাঁহার গর্দান উড়াইয়া দেওয়া হইবে”। বস্তুত ইহা ছিল হযরত উমর (রা)-এর সহজাত তেজোবীর্যেরই বাস্তব অভিব্যাক্তি মাত্র।
হযরত উমর (রা)-এর চরিত্রে যে তেজস্বিনী ও অনমনীয় ভাবধারা পূর্বাপর পরিলক্ষিত হয় কোন কোন সাহাবার উপর ইহার কিছুটা বিরুপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) যখন জীবনের শেষ পর্যায়ে উপনীত হইয়া পরবর্তী খলীফা নিয়োগের চিন্তায় অধীর হইয়া পড়েন, তখন তিনি ব্যক্তিগতভাবে হযরত উমর (রা)কে এই পদে অভিষিক্ত করার পক্ষে মত ব্যক্ত করেন। তিনি তাঁহার জীবনের দীর্ঘ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে নিঃসন্দেহে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন যে, তাঁহার অন্তর্ধানের পর উমর ফারুক (রা)-ই হইতেছেন খিলাফতের জন্য সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত ব্যক্তি। তিনি হযরত আবদুর রহমান বিন আউফ (রা)-এর নিকট যখন তাহার এই মত প্রকাশ করিলেন, তখন তিনি বলিলেনঃ ‘উমর ফারুক সম্পর্কে আপনার যে মত, আল্লাহ্র শপথ তিনি তাহা হইতেও উত্তম। কিন্তু চিন্তার বিষয় এই যে, তাঁহার প্রকৃতিতে তীব্রতা ও কঠোরতা অত্যন্ত বেশী’।(তাবারী) ইহার উত্তরে হযরত আবূ বকর (রা) বলিলেনঃ “ইহার কারণ এই যে, আমার মধ্যে ছিল অত্যধিক নম্রতা ও বিনয়। কিন্তু তাঁহার নিজের উপরই যখন দায়িত্ব অর্পিত হইবে, তখন তিনি তাঁহার অনেক অভ্যাস ও স্বভাবই পরিত্যাগ করিবেন। হে আবূ মুহাম্মাদ! আমার অভিজ্ঞতা এই যে, আমি কাহারো প্রতি ক্রুদ্ধ হইলে আমার ক্রোধাগ্নি নির্বাপিত করার জন্য উমরই চেষ্টিত হইতেন ও আমাকে নম্র ভাব অবলম্বনের পরামর্শ দিতেন’। (আল-ইসলাম অল-হিযারাতুল আরাবিয়া)।
হযরত উমর ফারুক (রা)-এর কঠোর প্রকৃতি সম্পর্কে হযরত আবূ বকর (রা)-কে জনগণের নিকটও জওয়াবদিহি করিতে হইয়াছে। তাঁহার পরবর্তী খলীফা সম্পর্কে তাঁহার মত যখন জনগণের মধ্যে প্রচারিত হইয়া পড়ে, তখন কিছু সংখ্যক লোক আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেঃ “উমরের মত কঠোর প্রকৃতির ব্যক্তিকে স্বীয় স্থলাভিষিক্ত করিলে আল্লাহ্র নিকট পৌঁছিয়া আপনি কি জবাব দিবেন?” হযরত আবূ বকর (রা) তাহাদের ভুল মতের অত্যন্ত সূক্ষ্ম পন্থায় প্রতিবাদ করিয়া বলিলেনঃ “আমি আল্লাহ্র সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিব যে, পরবর্তী উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম ব্যক্তিকেই আমি খলীফা হিসাবে পছন্দ করিয়াছি”।
বস্তুতঃনবী করীম (স)-এর দরবারে হযরত আবূ বকর (রা)-এর যে মর্যাদা ছিল, হযরত আবূ বকর (রা)-এর দরবারে অনুরূপ মর্যাদা ছিল হযরত উমর ফারুক (রা)-এর। (মুকদ্দমা ইবনে খালদুন ২০৬ পৃঃ) এইজন্য হযরত আবূ বকর (রা)-এর উপরোল্লিখিত উক্তি সম্পূর্ণ সত্য।
হযরত উমর (রা) খলীফা পদে অভিষিক্ত হওয়ার পর সর্বপ্রথম যে বাণী তাঁহার কণ্ঠনিঃসৃত হইয়া মুসলিম জনগণের কর্ণকুহরে প্রবেশ করে তাহা এইঃ ‘আরবগণ, রশি-বাঁধা উষ্ট্রের ন্যায় চালকের পশ্চাতে পশ্চাতে চলাই তোমাদের ধর্ম। কিন্তু চালক কোথায় কিভাবে লইয়া যায়, তাহাই লক্ষণীয়। তবে আমার সম্পর্কে বলিতে পারি-কা’বা ঘরের আল্লাহ্র কসম, আমি তোমাদিগকে অবশ্যই সঠিক পথে আনিয়া ছাড়িব’।
হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর দাফন কার্য সমাপ্ত হওয়ার অব্যবহিত পরই তিনি নিজ হস্ত হইতে মৃত্তিকা ঝাড়িয়া ফেলিয়া ভাষণ দানের জন্য দণ্ডায়মান হইলেন। সমবেত ইসলামী জনতাকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিলেনঃ
মুসলিম জনতা! আল্লাহ্ তোমাদিগকে ও আমাকে এক সাথে শামিল করিয়া দিয়াছেন। আর আমার প্রাক্তন দুই সঙ্গীর পর আমাকে জিন্দাহ ও অবশিষ্ট রাখিয়াছেন। আল্লাহ্ শপথ, আমার সম্মুখে যে সকল ব্যাপার উপস্থাপিত হইবে, তাহা সবই আমি মীমাংসা করিব। আর যাহা কিছু আমার অগোচরে থাকিয়া যাইবে, সেই বিষয়ে আমি পূর্ণ দায়িত্বজ্ঞান ও আল্লাহপরস্তি সহকারে চেষ্টা করিব। বস্তুতঃলোকেরা যদি আমার প্রতি ইহসান ও কল্যাণের আচরণ গ্রহন করে, আমিও তাহাদের সহিত অনুরূপ ব্যবহারই করিব। কিন্তু যদি কেহ খারাপ ও অবাঞ্ছনীয় আচরণ অবলম্বন করে, তাহা হইলে আমিও তাহাকে কঠোর শাস্তি দান করিব’।
হযরত উমর (রা)-এর এই নীতি-নির্ধারণী ভাষণই ছিল তাঁহার খিলাফতের কার্যসম্পাদনের দিক-নির্দেশিকা। অভিজ্ঞ লোকদের সুস্পষ্ট অভিমত এই যে, তিনি আগা-গোড়া তাঁহার এই কথা অনুযায়ীই কাজ করিয়াছেন। ইহার এক বিন্দু কমও করেন নাই, বেশীও করেন নাই।
হযরত উমর (রা) নিজেই আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করিতেনঃ
********(আরবী)
হে আল্লাহ্, আমি স্বভাবতই কঠোর প্রকৃতির লোক, আমাকে নম্র ও আর্দ্র করিয়া দাও। আমি দুর্বল, আমাকে শক্তি দান কর। আমি কৃপণ, আমাকে দানশীল বানাইয়া দাও। (আল ইসলাম অল-হিযারাতুল আরাবিয়া)
হযরত উমর (রা) খলীফা নিযুক্ত হওয়ার পর ইরাক অভিযানকে শক্তিশালী করার জন্য তিনি বিপুল সংখ্যক সৈন্য প্রেরণে উদ্যোগী হন। এই উদ্দেশ্য প্রকাশ্য জনসভায় উপর্যুপরি কয়েকদিন পর্যন্ত আবেদন করার পরও তিনি এক মর্মস্পর্শী ও উদ্দীপনাময় ভাষণ দান করে। উহার ফলে মুসলিম জনতা দলে দলে জিহাদে যোগদানের জন্য প্রস্তুত হয়। এই অব্যাহত সংগ্রামধারার শেষ পর্যায়ে ইরানের সঙ্গে মুসলমানদের প্রকাশ্য সংঘর্ষ ঘটে। কিন্তু মুসলিমগণ ইহাতে পরাজিত হন ও নয় সহস্র সৈনিকের মধ্যে মাত্র তিন সহস্র অবশিষ্ট থাকে। এই পরাজয়ের সংবাদ পাইয়া হযরত উমর ফারুক বেজায় অসন্তুষ্ট ও ক্রুদ্ধ হন। তখন তিনি ইসলামের জন্য আত্মদানের আহবান জানাইয়া যে জ্বালাময়ী বক্তৃতা করেন, আরব গোত্রসমূহের মধ্যে তাহা অগ্নুৎগীরণের সৃষ্টি করে। এমন কি অসংখ্য খৃস্টান নাগরিকও এই যুদ্ধে মুসলিমদের সহিত সংগ্রাম ক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়িতে প্রস্তুত হয়।
হযরত উমর ফারুক (রা)-এর খিলাফতকালে ইসলামের অপূর্ব বিজয় সাধিত হয়। মিশর, সিরিয়া, ইরাক, আর্মেনিয়া, ইরান, ফিলিস্তিন, আজারবাইজান,আলজিরিয়া ও ত্রিপলিতে এই সময় ইসলামের পতাকা উড্ডীন হয়। বস্তুতঃইহার পূর্বে যেমন এরূপ দেশ জয়ের কোন দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয় নাই, তেমনি ইহার পরেও নয়। তাঁহার নিক্ষিপ্ত কোন তীরই লক্ষ্যভেদে ব্যর্থ হয় নাই। তাঁহার উন্নত করা কোন ঝাণ্ডাই কখনো অবনমিত হয় নাই।
মুসলিমদের জীবন ছিল তাঁহার নিকট সর্বাধিক প্রিয় বস্তু। তিনি এমন সব লোককে সেনাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিতেন, সমসাময়িক সমাজে জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিচক্ষণতায় যাঁহাদের বিশেষ মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত ছিল। ‘নেহাওন্দ’ যুদ্ধে তিনি নু’মান বিন মাকরানকে লিখিয়াছিলেনঃ
আমি জানিতে পারিয়াছি যে, নেহাওন্দ শহরে অমুসলিম দুশমনগণ তোমাদের সহিত সংঘর্ষ বাধাইবার জন্য দলে দলে সমবেত হইতেছে। আমার এই চিঠি পাওয়া মাত্রই তোমার নিকটবর্তী মুসলিমগণকে লইয়া আল্লাহ্র আদেশ, সাহায্য ও রহমতের ছায়ায় যাত্রা করিবে। তাহাদিগকে বন্ধুর ও দুর্গম পথে লইয়া যাইবে না। কেননা উহাতে তাহাদের বিশেষ কষ্ট হইবে। তাহাদের সঙ্গত কোন অধিকারেই হস্তক্ষেপ করিবে না। অন্যথায় তাহারা অসন্তুষ্ট ও বিক্ষুব্ধ হইবে। তাহাদিগকে লইয়া নিবিড় অরণ্য পথেও প্রবেশ করিবে না। জানিয়া রাখিও,একজন মুসলিম ব্যক্তি এক লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা অপেক্ষাও আমার নিকট অধিকতর প্রিয় ও মূল্যবান।
তিনি এই অভূতপূর্ব দেশ জয়ের অভিযানে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য বিভিন্ন যুদ্ধে অসংখ্য সৈন্য প্রেরণ করিয়াছেন; কিন্তু যুদ্ধে কোন সিপাহী কিংবা সিপাহসালারের শাহাদাতের সংবাদ পাইলে তাঁহার দুই চক্ষুকটোর হইতে অবিশ্রান্ত ধারায় মর্মব্যথার তপ্ত অশ্রু বিগলিত হইয়া দরদর বেগে প্রবাহিত হইত, এমন কি সেই সঙ্গে কোন বিরাট দেশ জয়ের শুভ সংবাদ শুনাইলেও তাহা বারণ মানিত না।
হযরত উমর (রা) তাঁহার পূর্ববর্তী দুই মহান ব্যক্তির (রাসূলে করীম ও আবূ বকর সিদ্দীক)-এর মতই ন্যায়পরায়ণতা ও সততার নিশানবরদার ছিলেন। তাঁহার কণ্ঠনিঃসৃত বানীও ছিল তাঁহাদেরই অনুরূপ। বিদ্রোহী কুর্দজাতিকে দমন করার উদ্দেশ্য তিনি মুসলিমা আশজায়ীকে যখন প্রেরণ করেন, তখন তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলেনঃ
আল্লাহ্র নাম লইয়া রওয়ানা হইয়া যাও এবং আল্লাহ্র পথে আল্লাহ্দ্রোহী লোকদের সহিত পূর্ণ শক্তিতে লড়াই কর। তোমাদের মুশরিক ভাইদের সহিত সম্মুখ-সমর সংঘটিত হইতে থাকিলে প্রথমে তাহাদের নিকট তিনটি প্রস্তাব পেশ কর। তাহাদিগকে ইসলাম কবুল করার দাওয়াত দাও। তাহারা ইসলাম কবুল করিলে ও অস্ত্রসংবরণ করিয়া নিজেদের ঘরে বসিয়া থাকিতে প্রস্তুত হইলে তাহাদের ধনসম্পদ হইতে যাকাত আদায় করা তোমাদের কর্তব্য। তাহারা তোমাদের সহিত মিলিত হইয়া কাফিরদের বিরুদ্ধে লড়াই করিতে প্রস্তুত হইলে তাহাদের ও তোমাদের অধিকার ও মর্যাদা সমান হইবে। কিন্তু তাহারা যদি ইসলাম কবুল করিতে অস্বীকার করে,তবে তাহাদের নিকট আনুগত্য ও খারাজ প্রদানের দাবি জানাও। কিন্তু তাহাদের শক্তি-সামর্থের অধিক কোন বোঝা তাহাদের উপর চাপাইয়া দিওনা। খারাজ দিতে প্রস্তুত না হইলে তাহাদের সহিত লড়াই কর। আল্লাহ্ তাহাদের বিরুদ্ধে তোমাদের সাহায্য করিবেন।
হযরত উমর ফারুক (রা) প্রাদেশিক শাসনকর্তা ও বিভিন্ন বিভাগীয় সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে বিন্দুমাত্র আরামপ্রিয়তা, বিলাসিতা ও জাঁকজমক বরদাশত করতে প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি শাসক ও শাসিতের মধ্যে পূর্ণ ঐক্য ও সমতা রক্ষার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেন। অনারবদের বিলাসী সভ্যতা ও উচ্ছৃখল চরিত্র যেন তাহাদিগকে স্পর্শ করিতে না পারে, সেজন্য তাঁহার সংরক্ষণমূলক প্রচেষ্টার অন্ত ছিল না। শাসনকর্তা হযরত উৎবা বিন ফরকাদ (রা)- কে তিনি স্পষ্ট ভাষায় লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেনঃ বিলাসিতা, জাকঁজমক, সুখসম্ভোগ, মুশরিকী আচার ও রীতিনীতি এবং রেশমী বস্ত্র পরিহার করিয়া চলিবে।
নবনিযুক্ত শাসনকর্তাদের নিকট হইতে তিনি এই মর্মে প্রতিশ্রুতি গ্রহন করিতেন যে, তুর্কি ঘোড়ায় আরোহণ করিবে না, (কেননা ইহা তখনকার সময় চরম বিলাসিতারুপে বিবেচিত হইত), দ্বাররক্ষী নিযুক্ত করিবে না, অভাবগ্রস্ত ও প্রয়োজনশীল লোকদের জন্য দ্বার সতত উন্মুক্ত ও অবাধ রাখিবে। কেহ ইহার বিরুদ্ধাচরণ করিলে তিনি অনতিবিলম্বে তাহাকে পদচ্যুত করিতেন।
হযরত সায়াদ কুফা নগরে এক বিরাট প্রাসাদ নির্মাণ করেন। হযরত উমর (রা) উহাকে অগ্নি-সংযোগ করিয়া ভস্ম করিয়া ফেলেন। মিশরে হযরত খারেজা বিন হাজাফা এক বালাখানা তৈয়ার করেন। সংবাদ পাইয়া হযরত উমর (রা) উহাকে ধ্বংস করার নির্দেশ পাঠান। কেননা অন্যান্য অবৈধতা ছাড়াও উহার ফলে প্রতিবেশীর পর্দা বিনষ্ট হওয়ার আশংকা দেখা দিয়াছিল।(কিতাবুল খারাজ)
হজ্জের সময় মক্কা শরীফে উপস্থিত হইয়া উমর ফারুক (রা)শাসনকর্তাদের বিরুদ্ধে কোন প্রকার অভিযোগ থাকিলে তাহা সরাসরি তাঁহার নিকট পেশ করার আহবান জানাইয়া সাধারণ ঘোষণা প্রকাশ করিতেন। এক ব্যক্তি কোন শাসনকর্তার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করিল যে, সে তাহাকে অকারণ একশত চাবুকের আঘাত দিয়াছে। উত্তরে তিনি বলিলেন, সংশ্লিষ্ট শাসনকর্তাকে তুমি একশত চাবুক মারিবে।বস্তুত ইহা যে কত বড় কঠিন ফয়সালা, তাহা সহজেই অনুমেয়। সংশ্লিষ্ট শাসনকর্তা ইহাতে শিহরিয়া উঠিল। সে দাঁড়াইয়া বলিলঃ ‘এইরূপ করিলে শাসনকর্তার মর্যাদা নষ্ট হইবে ও শাসনকার্য অচল হইয়া যাইবে’। হযরত উমর (রা) বলিলেনঃ “তৎসত্ত্বেও এইরুপ সুবিচারের দৃষ্টান্ত স্থাপন অপরিহার্য কেননা স্বয়ং নবী করীম (স) এইরূপই করিয়াছেন’।
হযরত খালিদ ইবনে অলীদ (রা) কোন জাতীয় ও সামগ্রিক প্রয়োজন ব্যতীতই বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করিয়াছেন জানিতে পারিয়া হযরত উমর (রা)তাঁহাকে পদচ্যুত করার ফরমান প্রেরণ করেন। তিনি বলেনঃ “খালিদ এই অর্থ নিজ হইতে ব্যয় করিলে নিঃসন্দেহে অর্থের অপচয় করিয়াছেন আর বায়তুলমালের অর্থ ব্যয় করিয়া থাকিলে অনধিকার চর্চা ও আমানতে খিয়ানত করিয়াছেন”।
হযরত উমর (রা) পূর্ববর্তী মহান ব্যক্তিদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াই খিলাফতের কার্য সম্পাদন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেনঃ “আমার দুই সাথী ইতিপূর্বে অতীত হইয়াছেন। একই পথ ও পন্থাই তাঁহারা অবলম্বন করিয়াছিলেন। আমি তাঁহাদের বিপরীত কাজ করিলে তো আমার পক্ষে সম্পূর্ণ ভিন্ন পথ অবলম্বন করা হইবে”। বস্তুতঃ ইহা বিশ্বনবীর এই কথারই প্রতিধ্বনি মনে হয়ঃ ‘আমার পর কেহ নবী হইলে উমরই হইতেন সেই নবী’।
উমর ফারুক (রা)-এর চরিত্রে যে কঠোরতা ও অনমনীয় ভাবধারা পরিলক্ষিত হয়, স্বয়ং নবী করীম (স)-ই ইহার সঠিক ব্যাখ্যা দান করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেনঃ ‘আল্লাহ্র কার্যসমূহে উমর যত শক্ত ও কঠোর, আমার উম্মতের মধ্যে তত আর কেহ নয়’।
অপর একজন বলেন, ‘উমর সত্যের জন্য দানশীল; কিন্তু অন্যায় ও বাতিলের জন্য হাড়ে হাড়ে কৃপণ’।
বস্তুত হযরত উমর (রা) প্রকৃতির অন্ধ দাস ছিলনে না; তিনি কোন ব্যাপারে নিছক প্রকৃতিগত কঠোরতার দরুণই কঠোরতা অবলম্বন করিতেন, একথা কিছুমাত্র সত্য নহে; বরং কঠোরতা ও কোমলতা সম্পর্কে তাঁহার ধারণা অত্যন্ত সুস্পষ্ট ছিল, এ ব্যাপারে তাহার মন ও মগজ ছিল সর্বদা জাগ্রত। তাই তিনি নিজেই স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করিয়াছেনঃ
খিলাফতের কার্য যথাযথরূপে সম্পন্ন হইতে পারেনা যতক্ষণ না এমন কঠোরতা অবলম্বন করা হইবে, যাহা জুলুমের পর্যায় গিয়া পৌঁছায় না। এমন বিষয়েও নম্রতা অবলম্বিত হওয়া উচিত নহে, যাহার ভিত্তি দুর্বলতার উপর স্থাপিত। (কিতাবুল খারাজ)
আর এই কঠোরতাও ছিল সম্পূর্ণরূপে শরীয়াতের ব্যাপারে-আল্লাহ্র হক ও বান্দাহর হক-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু ব্যক্তিগত ব্যাপারে হযরত উমর (রা) কোন দিনই এক বিন্দু কঠোরতা প্রদর্শন করেন নাই। বরং সে ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন মোম অপেক্ষাও দ্রবীভূত ও কোমল। ঠিক এই কথাই জানা যায় উমর ফারুক (রা)-এর নিজের এক ভাষণ হইতে। তিনি প্রসঙ্গত বলিয়াছেনঃ
******(আরবী)
আল্লাহ্র শপথ, আমার দিল আল্লাহ্র ব্যাপারে যখন নরম হয়, তখন পানির ফেনা অপেক্ষাও অধিক নরম ও কোমল হইয়া যায়। আর আল্লাহ্র দ্বীন ও শরীয়াতের ব্যাপারেই (প্রয়োজন মুতাবিক) যখন শক্ত ও কঠোর হয়, তখন তাহা প্রস্তর অপেক্ষাও অধিক শক্ত ও দুর্ভেদ্য হইয়া পড়ে।
বস্তুত খিলাফতের দায়িত্ব সম্পাদনের ব্যপারে হযরত উমর ফারুক (রা) যে কঠোর নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা রাষ্ট্রনীতির দৃষ্টিতে ছিল একান্তই অপরিহার্য। হযরত খালিদ ইবনে অলীদকে পদচ্যুতকরণ, শাসনকর্তাদের সহিত কঠোরতা অবলম্বন, ইসলামী বিধান পালনে অত্যন্ত কড়াকড়ি অবলম্বন প্রভৃতি ক্ষেত্রে হযরত উমর (রা)-এর খিলাফতেরই ন্যায় বিরাট দায়িত্ব পাওনের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তিনি যাহা কিছু করিয়াছেন, খলীফা পদের কঠিন দায়িত্ব পালনের জন্যই করিয়াছেন। কেননা তাহা না করিলে খিলাফতের ন্যায় অতিশয় নাজুক ও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব কিছুমাত্র পালিত হইতে পারিত না। আর আল্লাহ্ না করুন, হযরত উমরও যদি খিলাফতের দায়িত্ব পালন করিয়া ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার বাস্তব নিদর্শন প্রতিষ্ঠা না করিতেন, তাহা হইলে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার বিলুপ্তিই ছিল অবধারিত।
তবে খিলাফতের দায়িত্ব পালনে তাঁহার কঠোরতা, অনমনীয়তা ও ক্ষমাহীনতা উমর চরিত্রের একটি দিকমাত্র। উহারই অপর দিকে হইল দয়া, সহানুভূতি ও ক্ষমা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে তাঁহার দৃষ্টান্তহীন অবদান। তদানীন্তন সমাজে আল্লাহ্র বিবেক-সম্পন্ন সৃষ্টিকুলের মধ্যে ক্রীতদাসদের তুলনায় অধিক দয়া ও সহানুভূতি লাভের অধিকারী আর কেহই ছিল না। হযরত উমর ফারুক (রা) খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহন করার পরই সমস্ত আরব ক্রীতদাসদের সম্পূর্ণ মুক্ত করিয়া দেন। সেই সঙ্গে তিনি এই মর্মে একটি শাসনতান্ত্রিক বিধানও জারী করেনঃ ‘আরববাসী কখনো কাহারো দাস বা গোলাম হইতে পারে না’। তদানীন্তন সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থানুযায়ী সমস্ত অনারব ক্রীতদাসকে মুক্ত করা বড়ই দুরূহ ব্যাপার ছিল। তা সত্ত্বেও তাহাদের পক্ষে কল্যাণকর বহু আইন-বিধান তিনি কার্যকর করেন। এমনকি মনিব-মালিকদের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের জন্যও তিনি সরকারী ভাতা বা বৃত্তি জারী করিয়া দেন।
হযরত উমর (রা) যিম্মী ও অমুসলিমদের সহিত এমন হৃদ্যতাপূর্ণ ও সম্মানজনক আচরণ গ্রহন করিয়াছিলেন, যাহা একালের মুসলমানরাও মুসলমানদের সহিত করেন না। এই ব্যাপারে তিনি জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বিশেষ সচেতন ছিলেন। সেই সঙ্গে তিনি সাধারণভাবে ক্ষমা ও অনুগ্রহ প্রদর্শনও বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করিতেন না।
দ্বিতীয় খলীফা সাধারণ জনকল্যাণমূলক কাজ কেবল সরকারী পর্যায়েই করিতেন, তাহা নয়। তিনি ব্যক্তিগতভাবেও মানবতার কল্যাণে সর্বক্ষণ কর্মে নিরত থাকিতেন। জিহাদের ময়দানে গমনকারী মুজাহিদদের বাড়ি বাড়ি গিয়া তিনি তাঁহাদের পরিবারবর্গের খবরাখবর লইতেন। কাহারো কোন প্রয়োজন দেখা দিলে তিনি সঙ্গে সঙ্গেই তাহা পূরণের ব্যবস্থা করিয়া দিতেন। কোথাও ভূক্ত লোক দেখিতে পাইলে অনতিবিলম্বে তাহাদের খাওয়ার ব্যবস্থা করিয়া দিতেন। উমর ফারুক (রা)-এর খিলাফত আমলে ধনী-দরিদ্র, নিঃস্ব ও ধনাঢ্যের মধ্যে পূর্ণ সমতা ও সাম্য স্থাপিত হইয়াছিল। জনগণের মধ্যে একবিন্দু বৈষম্যমূলক আচরণ প্রদর্শন না করার জন্য দায়িত্বশীল কর্মচারীদের প্রতি তিনি কঠোর নির্দেশ দিয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি নিজে কোনরূপ তোষামোদ ও তারীফ-প্রশংসা পছন্দ করিতেন না। মদীনার বিচারালয়ে তিনি বিবাদী হিসাবে উপস্থিত হইলে বিচারপতি খলিফাতুল মুসলেমীনের সম্মানার্থে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ইহা দেখিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ বলিলেনঃ ‘এই মামলায় ইহাই তুমি প্রথম অবিচার করিলে’। খলীফার দাপট ও প্রতাপে তখন গোটা পৃথিবী কম্পমান ছিল; কিন্তু তাঁহার অবলম্বিত সাম্য নীতির ফলে বিদেশী রাষ্ট্রদূতগণ আমিরুল মুমিনীনকে সহসা চিনিয়া লইতে পারিতেন না। তিনি অত্যন্ত তীব্র সম্ভ্রম বোধসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। পর্দাসংক্রান্ত আয়াত নাজিল হওয়ার পূর্বে সাধারণ মুসলিম মহিলারা তো বটেই,নবী করীম (স)-এর বেগমগণও পর্দা পালন করিতেন না। কিন্তু এই পর্দাহীনতা ও মহিলাদের অবাধ চলাফিরাকে তিনি তখনও পছন্দ করিতে পারিতেন না।
ফারুকী চরিত্রের মৌল ভিত্তি
হযরত উমর ফারুক (রা)-এর সুমহান চারিত্রিক গুণাবলী অত্যন্ত মজবুত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। উন্নততম নৈতিক মান প্রতিষ্ঠাকারী হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর নিবিড় ও ঘনিষ্টতম সাহচর্য হইতেই তিনি এই ভিত্তি অর্জন করিয়াছিলেন। ব্যক্তিগতভাবে তিনি ছিলেন মহৎ গুণাবলীতে বিভূষিত,নবী চরিত্রের বাস্তব প্রতিমূর্তি। তাঁহার চরিত্র-দর্পণে সর্বাধিক মাত্রায় প্রতিফলিত হইয়াছিল একনিষ্ঠতা, আল্লাহ্তে আত্মসমর্পণ, বৈষয়িক স্বাদ আস্বাদনে অনীহা, জিহ্বা ও মনের সংযম, ন্যায়পরায়ণতা, সত্যপরায়ণতা, বিনয় ও অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা। এই মহৎ গুণাবলী তাঁহার চরিত্রে এতই দৃঢ় ছিল যে, কোন লোক তাঁহার সংস্পর্শে আসিলে, তাঁহার চরিত্রেও এই গুণাবলী গভীরভাবে রেখাপাত করিত। তাঁহার নিকট হইতে প্রকৃত তাকওয়া পরহেজগারী শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্য বহু সাহাবীও অতীব উৎসাহে তাঁহার সংস্পর্শ লাভের জন্য চেষ্টিত হইতেন। স্বয়ং রাসূলে করীম (স) তাহার সম্পর্কে বলিয়াছেনঃ
*******(আরবী)
আল্লাহ্ ত’আলা উমরের মুখ ও দিলের উপর সত্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়াছেন। তিনি হইলেন হক্ক বাতিলের মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য বিধানকারী।
ফারুকী খিলাফত কালের সরকারী পদাধিকারীদের চরিত্রেও ইহার প্রভাব পুরামাত্রায় প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল।
আল্লাহ্ ভীতির তীব্রতা
উমর (রা)-এর চারিত্রিক দৃঢ়তার মূল উৎস ছিল আল্লাহ্র কুদরাত ও শক্তিমত্তার প্রতি দৃঢ় প্রত্যয়। তিনি নিতান্ত বিনয় ও ভীত-সন্ত্রস্ত হৃদয় লইয়া গভীর রাত্র পর্যন্ত নামাযে নিরত থাকিতেন। কুরআনের যে সব আয়াতে আল্লাহ্র মহানত্ত ও মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিয়া তিনি ভাবাবেগে অত্যন্ত আপ্লুত হইয়া যাইতেন এবং অদম্য কান্নায় ভাঙ্গিয়া পড়িতেন। তাঁহার হৃদয় এতই কোমল ও আর্দ্রতাপূর্ণ ছিল যে, একবার তিনি ফজরের নামাযে সূরা ইউসুফ পড়িতে শুরু করিলে তাঁহার হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিত এবং কাঁদিতে কাঁদিতেই সমগ্র কুরআন শেষ করিয়া রুকূতে যাইতে বাধ্য হইলেন।
কিয়ামত দিবসের পাকড়াওকে তিনি খুব বেশী ভয় পাইতেন। তিনি প্রায়শঃ বলিতেন, কিয়ামতের দিন জাহান্নামের আযাব হইতে কোনমতে রক্ষা পাইলেও নেকী-বদী সমান-সমান হইলেই আমি নিজেকে বড় সৌভাগ্যবান মনে করিব। একাবার একটি তৃণখণ্ড হাতে লইয়া তিনি দুঃখ-ভারাক্রান্ত কণ্ঠে বলিতে লাগিলেনঃ ‘হায়, আমি যদি এই তৃণখণ্ডের ন্যায় দায়িত্বমুক্ত হইতাম! হায়, আমি যদি ভূমিষ্ঠই না হইতাম! আল্লাহ্র ভয়ে তাঁহার হৃদয়-মন সব সময়ই ভীত-শঙ্কিত হইয়া থাকিত। এইজন্য তিনি প্রায়শঃবলিতেনঃঊর্ধ্বলোক হইতে যদি ঘোষিত হয় যে, দুনিয়ার একজন ছাড়া সমস্ত মানুষই জান্নাতী হইবে, তখনো আমার মনকে এই আশংকা কাতর ও আশংকাগ্রস্ত করিয়া রাখিবে যে, কি জানি, সেই হতভাগ্য ব্যক্তি আমিই না হইয়া পড়ি।
রাসূলের প্রতি ভালবাসা ও আনুগত্য
মন-মানসিকতার পরিচ্ছন্নতা ও পরিশুদ্ধি এবং উত্তম ও অকৃত্রিম চারিত্রিক গুন-বৈশিষ্ট্য অর্জনের জন্য মহৎ চরিত্রের মৌল উৎস বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর প্রতি ঐকান্তিক ভালোবাসা ও তাঁহার সুন্নাত অনুসরণ করিয়া চলার অকৃত্রিম নিষ্ঠা অর্জন একান্তই অপরিহার্য। বস্তুতঃযে দিল রাসূলের প্রতি প্রেমময় নয় এবং যে পদক্ষেপ রাসূলে করীম (স)-এর উত্তম আদর্শানুসারী নয়, তাহা ইহ-পরকালের নিয়ামত লাভে ধন্য হইতে পারে না। হযরত উমর ফারুক (রা) ছিলেন রাসূলের সত্যিকার নিষ্ঠাবান প্রেমিক। তিনি নিজের জান-মাল ও সন্তান-স্বজন অপেক্ষাও অধিক ভালবাসিতেন রাসূলে করীম (স)-কে। এই কারণে তিনি নবী করীম (স)-এর ইন্তেকালের ব্যাপারটিকে সহসা ও সহজভাবে স্বীকার করিয়া নিতে সক্ষম হন নাই।
হযরত উমর (রা) চরিত্রের সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল দিক হইল প্রতিপদে রাসূলে করীম (রা)-এর আক্ষরিক অনুসরণ। পানাহার, পোশাক-পরিচ্ছদ, উঠা-বসা,চলা-ফিরা,কথা-বার্তা প্রভৃতি সর্বকাজে তিনি নবী-আদর্শকে নিষ্ঠার সহিত অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন। রাসূলে করীম (স) অভাব-অনশন ও দারিদ্রের মধ্যে দিয়া জীবন অতিক্রম করিয়াছেন। এই জন্য হযরত উমর (রা) রোম ও পারস্যের বিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতি হইয়াও নিতান্ত দরিদ্রের ন্যায় জীবন অতিবাহিত করিতেন। একবার তাঁহার কন্যা উম্মুল মুমিনীন হযরত হাফসা (রা) বলিয়াছিলেনঃ ‘আল্লাহ্ তা’আলা এখন তো স্বাচ্ছন্দ্য ও প্রাচুর্য দান করিয়াছেন। কাজেই উত্তম পরিচ্ছদ ও উৎকৃষ্ট খাদ্য গ্রহন হইতে এখন আপনার বিরত থাকা উচিত নয়। জওয়াবে তিনি বলিলেনঃ ‘রাসূলে করীমের দুঃখ ও দারিদ্র-জর্জরিত জীবনের কথা কি তুমি ভুলিয়া গেলে? আল্লাহ্র শপথ, আমি তো আমার ‘নেতা’কে অনুসরণ করিয়াই চলিব। .........চলিব এই আশায় যে, পরকালে আল্লাহ্ আমাকে সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য দান করিবেন’।
রাসূলে করীম (স)-কে তিনি যে কাজ যেভাবে করিতে দেখিয়াছেন, সেই কাজটি ঠিক সেইভাবেই সম্পন্ন করিতে সব সময়ই চেষ্টিত থাকিতেন। তাঁহার কাজের ধরণ দেখিয়া উহার কারণ জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি অকপটে বলিয়া ফেলিতেনঃ “আমি রাসূলে করীম (স)-কে এই কাজটি ঠিক এইভাবে করিতে দেখিয়াছি বলিয়াই আমি ইহা এইভাবে করিলাম”।
দায়িত্বের তীব্র অনুভূতি
হযরত উমর (রা) স্বীয় দায়িত্ব ও কর্তব্যের ব্যপারে অত্যন্ত তীব্র অনুভূতিসম্পন্ন ছিলেন। জনগণের সব কিছুর জন্য তিনি নিজেকে দায়ী মনে করিতেন এবং সে দায়িত্ব পালনে যত কষ্টই হউক, তিনি তাহা অকাতরে বরদাশত করিতেন। মুসলিম জনগণ বা রাষ্ট্রের যে সব ধন-সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব তাঁহার উপর অর্পিত হইত, উহার জন্য তিনি চূড়ান্ত মাত্রায় কষ্ট ও শ্রম সহ্য করিতেন। বায়তুল মালের কোনরূপ ক্ষতি সাধিত হইলে তাহা পূরণ করিতেন এবং কোন কিছু হারাইয়া গেলে তাহা খুঁজিয়া বাহির করিতে যত শ্রমেরই প্রয়োজন হইত, ব্যক্তিগতভাবে তাহা স্বীকার করিতে তিনি একবিন্দু কণ্ঠিত হইতেন না।
হযরত আলী (রা) বলেন, একদা আমি হযরত উমর (রা)-কে উষ্ট্রে সওয়ার হইয়া দ্রুত চলিয়া যাইতে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলামঃ আমীরুল মু’মিনীন, আপনি কোথায় যাইতেছেন?’ জওয়াবে তিনি বলিলেনঃ ‘যাকাত বাবদ আদায় করা একটি উষ্ট্র হারাইয়া গিয়াছে, উহার খোঁজ করিতে বাহির হইয়াছি’। আমি বলিলামঃ এইরূপ করিয়া আপনি তো আপনার পরবর্তী খলিফাদের জন্য দায়িত্ব পালন অত্যন্ত কঠিন করিয়া দিতেছেন, অর্থাৎ আপনি খিলাফতের দায়িত্ব পালনে এতখানি কষ্ট স্বীকার করিলে আপনার পরে যাহারা খলীফা হইবেন,তাহাদিগকেও অনুরূপ কষ্ট করিতে হইবে। এই শুনিয়া তিনি বলিলেনঃ
*******(আরবী)
হে হাসানের পিতা! আমাকে তিরস্কার করিও না। যে আল্লাহ্ মুহাম্মাদ (স)-কে নবুয়্যাত দান করিয়া পাঠাইয়াছেন, তাঁহার শপথ; ফোরাত নদীর তীরে একটি উষ্ট্রও যদি মরিয়া যায়, তাহা হইলেও কিয়ামতের দিন সেজন্য এই উমরকেই পাকড়াও করা হইবে।
বস্তুতঃ অপরিসীম দায়িত্ববোধ এবং কিয়ামতের জওয়াবদিহির প্রতি অকৃত্রিম ও অবিচল বিশ্বাস থাকিলেই এইরূপ কথা বলা যায় এবং রাষ্ট্রীয় সম্পদ রক্ষার জন্য অনুরূপ চেষ্টা ও কষ্ট স্বীকার করা সম্ভব ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই।
হযরত উমর (রা) জনগণের প্রকৃত অবস্থা জানিবার জন্য রাত্রিকাল লোকালয়ে চলাফিরা করিতেন। তিনি একই ঘরে পরাপর তিন রাত্রি পর্যন্ত কান্নার ধ্বনি শুনিতে পাইয়াছিলেন। পরে তিনি ঘরে লোকদের ডাকিয়া শিশুর কান্নার কারণ জানিতে চাহিলেন। শিশুর মা বলিলঃ ‘স্তন সেবন বন্ধ না করা পর্যন্ত বায়তুল মাল হইতে শিশুর জন্য বৃত্তি বরাদ্দ করা হইবে না বিধায় অবিলম্বে দুগ্ধপোষ্য শিশুর স্তন সেবন বন্ধ করিতে চেষ্টা করা হইতেছে। শিশুর ইহাই মূল কারণ’।
এই কথা জানিতে পারিয়া অবিলম্বে তিনি ঘোষণা করাইলেনঃ
********(আরবী)
তোমারা শিশুর স্তন পান বন্ধ করার জন্যে তাড়াহুড়া করিও না। অতঃপর আমরা প্রত্যেক মুসলিম সন্তানের জন্যই খাদ্য বরাদ্ধ করিতেছি।
সেই সঙ্গে সমগ্র ইসলামী রাজ্যে এই বিধান অবিলম্বে কার্যকর করার জন্য তিনি স্পষ্ট নির্দেশ পাঠাইলেন।১ {দায়িত্ববোধের অনন্য দৃষ্টান্তঃএই প্রসঙ্গে আরেকটি ঐতিহাসিক ঘটনার কথা এখানে উল্লেখযোগ্য। একদা গভীর নিশিথে খলীফা উমর (রা) ইবনে আব্বাস(রা)-কে সঙ্গে লইয়া মদীনা হইতে দূরবর্তী এক পল্লী এলাকা পরিদর্শনে গেলেন। তাঁহারা একটি মহল্লার ভিতর দিয়া অতিক্রমের সময় পার্শ্ববর্তী জীর্ণ কুটিরের ভিতর হইতে শিশুদের ক্রন্দন-ধ্বনি শুনিতে পাইলেন। তাঁহারা কুটিরের ভিতর উঁকি মারিয়া দেখিলেনঃ এক বৃদ্ধা মহিলা উনুনে পানি ভর্তি হাঁড়ি বসাইয়া আগুন জ্বালাইতেছেন এবং উহার চারিপার্শ্বে বসিয়া শিশুরা ক্ষুধার জ্বালায় ক্রদন করিতেছে। মহিলা কিছুক্ষন থামিয়া থামিয়া শিশুদের প্রবোধ দিতেছেনঃ ‘তোমরা আরেকটু সবুর কর, এক্ষুণি খাবার তৈয়ার হইয়া যাইবে’। কিন্তু শেষ পর্যন্ত খাবার আর তৈয়ার হইল না। অনেক্ষন ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ক্লান্ত হইয়া অবশেষে শিশুরা ঘুমাইয়া পড়িল। মহিলাটিও একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া স্বগতোক্তি করিলঃ ‘যাক, আজিকার রাত্রের মত অন্ততঃ বাঁচা গেল’। এই মর্মান্তিক অবস্থা দেখিয়া খলীফা উমর (রা) এবং তাঁহার সহচর মহিলাটির মুখামুখি হইলেন তাঁহাদের প্রশ্নের জবাবে মহিলাটি, বলিলেনঃ ‘তাঁহার পরিবারে উপার্জনক্ষম কোন পুরুষ সদস্য নাই; তিনি নিজেও উপার্জন করিয়া শিশুদের মুখে অন্ন যোগাইতে পারিতেছেন না। তাই কয়েকদিন যাবত তিনি উনুনে শুধু পানিভর্তি হাঁড়ি বসাইয়া ক্ষুধার্ত শিশুদের এইভাবে প্রবোধ দিতেছেন’। তাঁহার প্রশ্ন করিয়া আরো জানিতে পারিলেন যে, রাষ্ট্রের বায়তুল মাল হইতে এ পর্যন্ত তাহাদের নিকট কোন খাদ্য-সাহায্য পৌঁছে নাই। এই মর্মভেদী কাহিনী শুনিয়া খলীফা এবং তাহার সহচর দ্রুত মদীনা পৌঁছিয়া বায়তুল মালের গুদামের দরজা খুলিলেন। অতঃপর তিনি নিজেই এক বস্তা ময়দা ও একবস্তা চিনি কাঁধে তুলিয়া দরিদ্র মহিলাটির উদ্দেশে রওয়ানা হইলেন। এই সময় ইবনে আব্বাস (রা) অন্ততঃএকটি বস্তা তাঁহার কাঁধে তুলিয়া দেওয়ার জন্য খলিফাকে অনুরোধ করিলেন। খলীফা উহা দ্বীর্থহীন ভাষায় প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিলেনঃ ‘ইবনে আব্বাস! আজ তুমি আমার বোঝা হাল্কা করিবার জন্য আগাইয়া আসিয়াছ;কিন্তু কিয়ামতের দিন যখন দায়িত্ব পালনের যখন দায়িত্ব পালনের এই ব্যর্থতার জন্য আমাকে অভিযুক্ত করা হইবে তখন তো তুমি আমার পাপের বোঝা হাল্কা করিতে আগাইয়া আসিবেনা’। দ্বিতীয় খলীফার দায়িত্ববোধ কত প্রখর ছিল, এই ঘটনা উহার জ্বলন্ত প্রমাণ।– সম্পাদক }
এই মানবিকতা, সহানুভূতি ও পরদুঃখ কাতরতা ইসলামী আদর্শ-ভিত্তিক রাষ্ট্র নায়কদের চরিত্রে প্রকট থাকাই বাঞ্ছনীয়।
হযরত উমর (রা) বস্তুতঃই সমাজের প্রতিটি দুর্বল ও ইয়াতীম ব্যক্তির জন্য স্নেহ-বাৎসল্যপূর্ণ পিতার সমতুল্য ছিলেন। সুবিচার ও ন্যাপরায়নতাই ছিল তাঁহার প্রধান বৈশিষ্ট্য। তিনি স্বাধীনতা ও সাম্যের প্রতি সমান গুরুত্ত স্বীকার করিতেন। ১ {স্বাধীনতার প্রশ্নে আপোষহীনতাঃ মানুষের স্বাধীনতা তথা মৌল মানবাধিকার প্রশ্নে হযরত উমর (রা)-এর মনোভাব ছিল আপোষহীন। কোন যুক্তিগ্রাহ্য ও আইনসঙ্গত কারণ ব্যতীত কাহারো স্বাধীনতা এতটুকু ক্ষুণ্ণ করার তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না। এ ব্যাপারে শাসনকর্তাদের প্রতি ও ছিল তাঁহার কড়াকড়ি নির্দেশ। এতৎসত্ত্বেও একবার খলীফার নিকট মিশরের শাসনকর্তার বিরুদ্ধে এই মর্মে অভিযোগ আসিল যে, তিনি (শাসনকর্তা) কোন যুক্তিগ্রাহ্য ও আইনসম্মত কারণ ছাড়াই নেহায়েত সন্দেহের বশে কতিপয় ব্যক্তিকে কারাগারে আটক করিয়া রাখিয়াছেন।খলীফা অবিলম্বে শাসনকর্তাকে ডাকাইয়া আনিয়া ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। শাসনকর্তা ইহার কোন সদুত্তর দিতে পারিলেন না। তখন খলীফা তাহাকে তিরস্কার করিয়া বলিলেনঃ ‘এই লোকগুলিকে তো ইহাদের মায়েরা স্বাধীনভাবেই প্রসব করিয়াছিল। তুমি ইহাদের পরাধীন করিয়া রাখার অধিকার কোথায় পাইলে?’ বস্তুতঃ জীবনের শেষ মুহূর্ত অবধি এই বলিষ্ঠ নীতিভঙ্গির উপরই খলীফা উমর (রা) অবিচল ছিলেন। ইহা হইতে কেহ তাঁহাকে একবিন্দু টলাইতে পারে নাই।–সম্পাদক}
সমাজের দুর্বল ও মিসকীনদের কাতারে দাঁড়াইয়া তিনি মানব জাতির সার্বিক কল্যাণের জন্য কাজ করিতেন। কেবল মুসলমানেরা প্রতিই তাঁহার এই নীতি কার্যকর ছিল না। ইসলামী রাজ্যের অনুগত অমুসলিম নাগরিকদের প্রতিও তিনি বিন্দুমাত্র পার্থক্যবোধ রাখিতেন না। তিনি তাহাদের প্রতি সুবিচারপূর্ণ আচরণ ও ন্যায়নীতি অনুসরণ করার জন্য সকল পর্যায়ের প্রশাসকদের প্রতি নির্দেশ জারী করিয়াছিলেন। তাহাদের প্রতি সকল প্রকার অন্যায় ও জুলুমমূলক আচরণ পরিহার করার জন্য তিনি তাকীদ করিতেন। এই পর্যায়ে তাঁহার নিজেরই একটি ঐতিহাসিক উক্তি বিশেষভাবে উল্লেখ্য।তিনি বলিয়াছিলেনঃ
********(আরবী)
আল্লাহ্ তা’আলা আমার উপর যে দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছেন, তাহার কল্যাণ প্রধানতঃ তিনটি জিনিসের উপর নির্ভরশীল। তাহা হইলঃ আমানত বা বিশ্বস্ততা যথাযথভাবে রক্ষা করা, শক্তি সহকারে উহা ধারণ করা এবং আল্লাহ্র নাজিলকৃত বিধান অনুযায়ী শাসন ও বিচার কার্য সম্পাদন করা।
রাষ্ট্রীয় ধনমাল সম্পর্কে তিনি বলিয়াছিলেনঃ
*******(আরবী)
তোমরা জানিয়া রাখ, এই রাষ্ট্রীয় ধন-মালের কল্যাণ মাত্র তিন প্রকার ব্যবহারে নিহিতঃ উহা গ্রহণ করা হইবে হক্কভাবে- হক্ক অনুসারে, দেওয়া হইবে হক্কভাবে অর্থাৎ হক্ক আদায় স্বরূপ এবং বাতিল পন্থায় গ্রহন বা দান বন্ধ। দুর্বল ঈমানদার লোকের পক্ষে শাসন-বিচারে সুবিচার বাস্তবায়িতকরণই যথেষ্ট।
বিচার কার্যে তিনি সুবিচার প্রতিষ্ঠার জন্য কায়মনোবাক্যে প্রস্তুত হইতেন। দুই বিবদমান পক্ষ বিচার পাওয়ার উদ্দেশ্যে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে তিনি দুই হাঁটু বিছাইয়া মহান আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করিতেন এই বলিয়াঃ
হে আল্লাহ্, তুমি এই কাজে আমাকে সাহায্য কর। কেননা পক্ষদ্বয়ের প্রত্যেকেই আমাকে আমার দ্বীন হইতে বিভ্রান্ত করিয়া দিতে পারে।–(যদি আমি ন্যায়বিচার না করি)।
ভোগ-বিলাসে অনীহা ও অল্পোতুষ্টি
বৈষয়িক স্বাদ-আস্বাদনের লোভ-লালসাই প্রকৃতপক্ষে অনৈতিকতা চরিত্রহীনতা ও দুর্নীতি সৃষ্টির মূল কারণ। এই জন্য হযরত উমর ফারুক (রা) স্বভাবতঃই উহা ঘৃণা করিতেন।তাঁহার সমসাময়িক লোকেরা একবাক্যে স্বীকার করিতেন যে, ভোগ-বিলাসে অনীহা ও অল্পে তুষ্টির ক্ষেত্রে তিনি সকলকে ছাড়াইয়া গিয়াছেন। রাসূলে করীম (স) কোন সময় তাঁহাকে কিছু দিতে চাহিলে তিনি বলিতেনঃ “হে রাসূল! আমার চেয়ে অভাবগ্রস্ত লোক অনেক রহিয়াছে। তাহারাই ইহা পাইবার অধিক যোগ্য”। হযরত উমর (রা)-এর দেহ কখনও নরম মসৃণ পোশাক স্পর্শ করে নাই। খণ্ড খণ্ড তালিযুক্ত কোর্তা,জীর্ণ-দীর্ণ কাপড়ের পাগড়ী, এবং ছিন্ন-চূর্ণ জুতা-ইহাই ছিল তাঁহার আজীবনের ভূষণ। ইহা লইয়াই তিনি কাইজার ও কিসরার রাষ্ট্রদূতদের এবং দেশ-বিদেশের প্রতিনিধিবর্গের সহিত সাক্ষাত করিতেন। তাঁহার নিকৃষ্ট মানের খাবার দেখিয়া লোকেরা স্তম্ভিত ও হতবাক হইয়া যাইত। তিনি বলিতেনঃ ‘তোমরা কি মনে কর আমি উৎকৃষ্ট ও সুস্বাদু খাবার গ্রহনে অক্ষম ও অনিচ্ছুক?আল্লাহ্র শপথ, কিয়ামতের দিবসের ভয় না হইলে আমিও তোমাদের ন্যায় ভোগ-বিলাস ও স্বাদ-আস্বাদনে নিমগ্ন হইতাম’। তিনি সরকারী দায়িত্তে নিযুক্ত কর্মচারীদিগকেও অনুরূপ ভোগ-বিলাস ও স্বাদ-আস্বাদন হইতে বিরত থাকার জন্য কড়া নির্দেশ দিতেন।
অল্পেতুষ্টি ছিল তাঁহার স্বভাবগত গুন। খলীফা নিযুক্ত হওয়ার পর ক্রমাগত কয়েক বৎসর পর্যন্ত তিনি বায়তুলমাল হইতে একটি মুদ্রাও গ্রহণ করেন নাই।অথচ অভাব-অনটন ও দারিদ্রের কষাঘাতে তাঁহার গোটা পরিবারই বিধ্বস্ত হইয়া যাইতেছিল। সাহাবায়ে কিরাম তাঁহার এই অবস্থা দেখিয়া অতি সাধারণ খাদ্য ও পোশাক সংগ্রহ হইতে পারে এমন পরিমাণ ভাতা বায়তুল মাল হইতে তাঁহাকে প্রদানের ব্যবস্থা করিয়া দেন। কিন্তু হযরত উমর (রা) উহা গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন এই শর্তে যে, ‘যতদিন প্রয়োজন ঠিক ততদিনই ভাতা গ্রহন করিতে থাকিব। আমার নিজের আর্থিক অবস্থা সচ্ছল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উহা লওয়া বন্ধ করিয়া দিব’। তখন রুবাই ইবনে জিয়াদ হারেমী বলিলেনঃ ‘আমীরুল মু’মিনীন! আল্লাহ্ তা’আলা আপনাকে যে মর্যাদা দান করিয়াছেন, তাহাতে আপনি দুনিয়ার সকলের অপেক্ষা অধিক বিলাস-ব্যসন, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও আনন্দ-স্ফূর্তির জীবন যাপনের অধিকারী’। হযরত উমর (রা)ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেনঃ ‘আমি তো জনগণের আমানতদার মাত্র। আমানতের খিয়ানত করা কি কখনো জায়েয হইতে পারে?’ হযরত উৎবা(রা) একদিন তাঁহাকে নিকৃষ্ট মানের খাদ্য খাইতে দেখিয়া বলিলেনঃ আমীরুল মু’মিনীন! খাওয়া-পরার ব্যাপারে আপনি যদি কিছুটা বেশী পরিমাণ ব্যয় করেন, তাহাতে মুসলমানদের সম্পদ কম হইয়া যাইব না’। হযরত উমর (রা)বলিলেনঃ ‘বড়ই দুঃখের বিষয়, তুমি আমাকে বৈষয়িক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও বিলাস-ব্যসনে প্রলোভিত করিতেছ’।
বস্তুত খিলাফতের দায়িত্ব অর্পিত হওয়ার পর হযরত উমর (রা)জীবন যাত্রার ব্যাপারে অত্যধিক সতর্কতা অবলম্বন করেন। কেননা এই সময় তাঁহার সামান্য ভুল-ত্রুটি প্রকাশ পাইলেও উহা সমগ্র মুসলিম জনতার চরিত্রে দুর্নীতি প্রশ্রয় পাওয়ার কারণ হইয়া দাঁড়াইতে পারিত।
হযরত উমর ফারুক (রা)-এর খিলাফত
হযরত উমর ফারুক (রা)-এর দশ বৎসরকালীন শাসন আমলে ইসলামী খিলাফত চরম উৎকর্য ও অদৃষ্টপূর্ব অগ্রগতি লাভ করে। রোম ও পারস্যের ন্যায় শক্তিশালী রাষ্ট্রদ্বয় এই সময়ই মুসলমানদের অধিকারভুক্ত হয়। বস্তুতঃমুষ্টিমেয় মরুবাসী অতি অল্প সময়ের মধ্যে যে বিপ্লব সৃষ্টি করিয়াছিল, ইতিহাস উহার দৃষ্টান্ত পেশ করিতে অক্ষম। আলেকজান্ডার দি গ্রেট, চেঙ্গিস খান ও তৈমূর লং সমগ্র পৃথিবী গ্রাস করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছিলেন এবং ভূ-পৃষ্ঠকে তাঁহারা তছনছ করিয়া দিয়াছিলেন; কিন্তু দ্বিতীয় খলীফার আমলের দেশজয় ও রাজ্যাধিকারের সহিত উহার কোন তুলনা হইতে পারে না। প্রথমোক্ত ব্যক্তিগণ এক সর্ব-বিধ্বংসী ঝড়ের ন্যায় একদিক হইতে উথিত হইয়া অত্যাচার-নিষ্পেষণ ও রক্তপাতের সয়লাব সৃষ্টি করিয়া অন্যদিকে চলিয়া গিয়াছেন। আলেকজান্ডার সিরীয় রাজ্যর “ছুর” নগর অধিকার করিয়া এক সহস্র নাগরিক নির্মমভাবে হত্যা করেন। সেই সঙ্গে তিনি ত্রিশ সহস্র নাগরিককে দাস-দাসীতে পরিণত করিয়া বিক্রয় করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই।
কিন্তু হযরত উমর ফারুক (রা)-এর আমলে যে সব দেশ ও শহর-নগরের উপর ইসলামী খিলাফতের পতাকা উত্তোলিত হয়, সেইসব স্থানে জুলুম-নিষ্পেষণ ও নির্যাতনের একটি দৃষ্টান্তও খুঁজিয়া পাওয়া যাইতে পারে না। ইসলামী সৈন্যবাহিনী বিশেষভাবে আদিষ্ট হইয়াছিল এই জন্য যে, তাহারা যেন শিশু, বৃদ্ধ ও নারীর উপর কোন প্রকার হস্তক্ষেপ না করে। ব্যাপক ও সাধারণ নরহত্যা তো দূরের কথা,সবুজ-শ্যামল বৃক্ষরাজি পর্যন্ত কর্তন করাও ইসলামী সেনাদের জন্য কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ছিল। মুসলিম শাসকগণ বিজিত অঞ্চলে ইনসাফ,ন্যায়পরায়ণতা ও সৌজন্যের যে অপূর্ব দৃষ্টান্ত স্থাপন করিতেন, তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া সকলেই মুগ্ধ ও আকৃষ্ট হইত। ফলে ইসলামী খিলাফতী শাসনকে তাহার অপূর্ব রহমত বলিয়া মনে করিত এবং এই রহমত অবিলম্বে তাহাদের দেশ ও জাতির উপর বর্ষিত হইবার জন্য তাহারা রীতিমত প্রার্থনা করিত। এমনকি, তাহারা কৃতজ্ঞতার আতিশয্যে বিজয়ী মুসলমানদিগকে বিশেষ সাহায্য ও সহযোগিতা করিতেও কুণ্ঠিত হইত না। সিরিয়া বিজয়ের ব্যাপারে স্বয়ং সিরিয়াবাসী অমুসলিম জনগণই স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া মুসলমানদের পক্ষে সংবাদ সরবরাহ ও খোঁজ-খবর দেওয়ার কাজ করিয়াছেন। ইরাক বিজয়-কালে তথাকার অনারব জনতা ইসলামী সৈনিকদের জন্য স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া পুল নির্মাণ করে এবং প্রতিপক্ষের গোপন তথ্যাদি সংগ্রহ করিয়া পরিস্থিতির মুকাবিলা করিবার জন্য প্রস্তুত হইবার সুযোগ দেয়। এই সকল পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে হযরত উমর ফারুক (রা)-এর সহিত আলেকজান্ডার দি গ্রেট ও চেংগীজ খানের মত রক্তপাতকারীদের যে কোন তুলনাই হইতে পারে না,তাহা বলাই বাহুল্য।
আলেকজান্ডার ও চেংগীজের রক্তপাত হয়ত তদানীন্তন সমাজে সাময়িকভাবে কোন ফল দান করিয়া থাকিতে পারে; কিন্তু যে রাষ্ট্রের বুনিয়াদই স্থাপিত হয় অত্যাচার-নিষ্পেষণ ও রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের উপর,তাহা সাধারণভাবে মানব সমাজের জন্য কোন স্থায়ী কল্যাণ বহন করিয়া আনিতে পারে না, তাহা নিঃসন্দেহে। বিশেষতঃউল্লেখিত ঘটনাবলির প্রেক্ষিতে এই কথাটি পুরাপুরি প্রযোজ্য হইতে পারে। বর্তমানে এইসব বিশ্ববিজয়ী বীরদের নাম-নিশানা পর্যন্ত কুত্রাপি পরিলক্ষিত হয় না। কিন্তু উমর ফারুক (রা) যে সুবিশাল ইসলামী-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, সুবিচার, ইনসাফ, সহনশীলতা, সাম্য ভ্রাতৃত্ব, উদারতা ও সহানুভূতির মহত গুণরাজি তাহাতে পূর্ণমাত্রায় বিকশিত হইয়াছিল। এই কারণে বিশ্ব-ইতিহাসে ফারুকী খিলাফত যথার্থই এক স্বর্ণ-যুগ ও মানবতার প্রকৃত কল্যাণের যুগে বলিয়া অভিহিত হইতেছে।
খিলাফতের রাষ্ট্র-রূপ
ইসলামের খিলাফতী শাসন ব্যবস্থা যদিও হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর সময় হইতেই সূচিত হয় এবং তাঁহার সংক্ষিপ্ত শাসনকালে ইহার ভিত্তি রচনা করা হয়; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর ফারুক (রা) এর সময়ই সূচিত হয় একটি সুষ্ঠু ও সুসংবদ্ধ রাষ্ট্রব্যবস্থা। এই সময়ই খিলাফতের বিকশিত রূপ বিশ্ববাসীকে মুগ্ধ ও আকৃষ্ট করে। তাঁহার আমলে কাইসার ও কিসরার বিরাট রাষ্ট্রদ্বয়ই যে মুসলমানদের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল তাহাই নয়, সেই সঙ্গে ইসলামী খিলাফতী রাষ্ট্র ও সরকার নিজ নিজ মর্যাদা ও দায়িত্ব সহকারে পূর্ণমাত্রায় কার্য সম্পাদনের সুযোগ লাভ করে। বস্তুতঃএকটি আধুনিক উন্নত রাষ্ট্রের যতগুলি দিক ও বিভাগ থাকিতে পারে, ফারুকী খিলাফতে উহার প্রায় সব কয়টিই যথাযথরূপে বর্তমান ছিল।
হযরত উমর (রা)-এর খিলাফতকালে পাক-ভারত উপমহাদেশের সীমান্ত হইতে মিশর ও সিরিয়া পর্যন্ত সমগ্র এলাকার উপর ইসলামী পতাকা উড্ডীন হইয়াছিল। এই বিশাল অঞ্চলে বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন ভাষাভাষী লোক বসবাস করিত। হযরত উমর (রা)-এর ঐকান্তিক প্রচেষ্টা নিয়োজিত ছিল আরব ও অনারব মুসলমানদিগকে সর্বতোভাবে একজাতি ও এক মনা রূপে গড়িয়া তোলার উদ্দেশ্য। ইসলামী জীবন-দর্শন ও ঈমানী ভাবধারা এই বিরাট অঞ্চলের অধিবাসীদিগকে একই সূত্রে গ্রথিত করিয়া দিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাদের গোত্রীয় জীবনের ধারা তখনো পুর্ববৎই উদ্দাম গতিতে প্রবাহিত ছিল। হিংসা-দ্বেষের জাহিলী ভাবধারা কোন কোন ক্ষেত্রে মাথাচাড়া দিয়া উঠিতেও চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু উমর ফারুক (রা)-এর কঠোরতর আদর্শনিষ্ঠা ও নীতিবাদিতা জাহিলিয়াতের স্তূপীকৃত আবর্জনা অপসারিত করিবার জন্য প্রতি মুহূর্ত চেষ্টিত ছিল। হযরত উমর (রা) সমগ্র ইসলামী রাজ্যের অধিবাসীদিগকে একদিল, একমগজ ও এক লক্ষ্যাভিসারী একটি জাতি রূপে গড়িয়া তুলিতে এবং ইসলামের দুশমনদের মুকাবিলায় তাহাদিগকে সুসংবদ্ধ ও সংগ্রামমুখর করিয়া গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন। পরন্তু যেসব মুসলমান বিভিন্ন কার্যব্যাপদেশে দুনিয়ার অন্যান্য দেশ ও জাতির মধ্যে গিয়া বসবাস করে, তাহারা যাহাতে নিজেদের বৈশিষ্ট্য ও সান্তত্র্য নষ্ট করিয়া ভিন্ন জাতির সহিত মিলিয়া একাকার হইয়া না যায়, সেদিকে তাহার সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল। তিনি সমগ্র আরব দেশকে ইসলাম-দুশমন লোকদের পঙ্কিলতা হইতে সম্পূর্ণ পবিত্র করিয়া তোলেন। তিনি তাঁহার বিশেষ দূরদৃষ্টির ফলে ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার বুনিয়াদ সুদৃঢ়করণ ও মুসলমানদের অর্থনৈতিক উন্নতি বিধানের জন্য কৃষিব্যবস্থার সংস্কার ও উন্নয়ন সাধন করেন। এই জন্য তিনি ইসলামী রাষ্ট্রের মধ্যে কৃষিজমির ক্রয়-বিক্রয় ও বিলি-বিতরণ বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত ভিন্ন জাতির চাল-চলন, রীতি-নীতি ও সভ্যতা-সংস্কৃতি গ্রহন করা সম্পর্কে তিনি মুসলমানদিগকে সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন। তাহাদের জীবন রাসূলে করীম (স)-এর জীবন অনুসারে গড়িবার জন্য সাধারনভাবেই তিনি সকলকে উপদেশ ও নির্দেশ দিতেন
ফারুকী খিলাফতের কাঠামো
হযরত উমর ফারুক (রা)-এর খিলাফত ছিল পূর্ণ মাত্রায় একটি গন-অধিকার-ভিত্তিক রাষ্ট্র। তাঁহার আমলে দেশের যাবতীয় সমস্যা মজলিসে শু’রার সম্মুখে পেশ করা হইত। কুরআন সুন্নাহ ও প্রথম খলীফার অবলম্বিত রীতিনীতিকে সম্মুখে রাখিয়া প্রতিটি বিষয়ে চূড়ান্ত ফয়সালা করা হইত। মজলিসে শু’রায় কখনো সর্বসম্মতভাবে আর কখনো অধিকাংশ লোকের মতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হইত। নিম্নলিখিত সাহাবীগণ তাঁহার মজলিসে শু’রার প্রধান সদস্য ছিলেনঃহযরত উসমান (রা), হযরত আলি(রা), হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা), হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রা),হযরত উবাই ইবনে কায়াব (রা) ও হযরত জায়েদ ইবনে সাবিত (রা)।
এই মজলিসে শু’রা ব্যতীত একটি সাধারণ মজলিসও তাঁহাকে পরামর্শদান ও রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মীমাংসার জন্য বর্তমান ছিল। মুহাজির ও আনসারদের সকল সাহাবী ছাড়াও গোত্রীয় সরদারগণও ইহাতে যোগদান করিতেন। বিশেষ গুরুত্ববহ ও সংকটপূর্ণ মুহূর্তে এই সাধারণ মজলিসের অধিবেশন আহ্বান করা হইত। অন্যথায় দৈনন্দিন কার্য সম্পাদনের জন্য কেবলমাত্র মজলিসে শু’রার ফয়সালার উপরই তাঁহাকে নির্ভর করিতে হইত এবং উহার ফয়সালাই চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইত। এই মজলিসদ্বয় ব্যতীত আরো একটি মজলিস তখন কার্যরত ছিল, যাহাকে ‘মজলিসে খাস’ বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। ইহাতে কেবলমাত্র মুহাজির সাহাবিগণই যোগদান করিতেন।
গণ-অধিকারসম্মত রাষ্ট্র বলিতে সেই ধরণের রাষ্ট্র-সরকার বুঝায়, যেখানে প্রতিটি নাগরিকই তাহার যাবতীয় অধিকার ভোগের সুযোগলাভ করিতে পারে;যেখানে প্রত্যেকই নিজস্ব মতামত প্রকাশ করিতে ও অন্যদের জানাইতে পারে। হযরত উমর (রা)-এর খিলাফতে এই সকল বৈশিষ্ট্য পুরামাত্রায় কার্যকর ছিল। সেখানে প্রতিটি ব্যক্তিই পূর্ণ স্বাধীনতা সহকারে নিজ নিজ অধিকার দাবি করিতে পারিত।
হযরত উমর ফারুক (রা) খলীফা নির্বাচিত হওয়ার পর তাঁহার খিলাফতের মৌল-নীতিমালা ঘোষণা করিয়া যে গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দান করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছিলেনঃ
*********(আরবী)
তোমাদের ধন-সম্পদে আমার অধিকার ততটুকু যতটুকু অধিকার স্বীকৃত হয় ইয়াতীমের মালে উহার মুতাওয়াল্লীর জন্য। আমি যদি ধনী ও সচ্ছল অবস্থায় থাকি, তবে আমি কিছুই গ্রহন করিব না আর যদি গরীব হই, তবে প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী জরুরী পরিমাণ গ্রহন করিব। ১ {অপর একটি বর্ণনার ভাষা এই ****(আরবী) ‘আমি আমার নিম্নতম প্রয়োজন গ্রহন করিব’।}
হে লোকসকল, আমার উপর তোমাদের কতকগুলি অধিকার রহিয়াছে, আমার নিকট হইতে তাহা আদায় করা তোমাদের কর্তব্য। প্রথম, দেশের রাজস্ব ও গণিমতের মাল যেন অযথা ব্যয় হইতে না পারে, দ্বিতীয় তোমাদের জীবিকার মান-উন্নয়ন ও সীমান্ত সংরক্ষণ আমার কর্তব্য। আমার প্রতি তোমাদের এই অধিকারও রহিয়াছে যে, আমি তোমাদিগকে কখনও বিপদে নিক্ষেপ করিব না।
অপর এক ভাষণে তিনি বলিয়াছেনঃ ‘তোমাদের যে কেহ আমার মধ্যে নীতিবিচ্যুতি দেখিতে পাইবে, সে যেন আমাকে সঠিক পথে পরিচালিত করিতে চেষ্টা করে’। উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দের মধ্য হইতে একজন দাঁড়াইয়া বলিলঃ ‘আল্লাহ্ শপথ, তোমার মধ্যে আমার কোন নীতিবিচ্যুতি দেখিতে পাইলে এই তীব্রধার তরবারি দ্বারা উহাকে ঠিক করিয়া দিব’।
হযরত উমর (রা) এই জওয়াব শুনিয়া শোকর আদায় করিলেন ও বলিলেনঃ ‘আল্লাহ্ এই জাতির মধ্যে এমন লোক তৈয়ার করিয়াছেন,যাহারা তাঁহার নীতিবিচ্যুতির সংশোধন করিতে পারেন। এই জন্য আমি আল্লাহ্র শোকর আদায় করিতেছি’।
এই ভাষণ কতকগুলি আকর্ষণীয় শ্লোগান তেজব্যঞ্জক শব্দেরই সমষ্টি নহে; বস্তুতঃইহাই হইতেছে ইসলামী খিলাফতের মেনিফেষ্টো বা নীতিমালা। খলীফা ফারুকে আযম (রা) এই নীতিমালা খুব দৃঢ়তা সহকারেই পালন করিতেন। তাই দেখা যায় আমীরুল মু’মিনীন অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন; কিন্তু ঔষধ হিসাবে ব্যবহার করার জন্য বায়তুল মাল হইতে সামান্য পরিমাণ মধুও কেবলমাত্র এইজন্য গ্রহণ করিলেন না যে, পূর্বাহ্ণে জনগণের নিকট হইতে উহার অনুমতি লওয়া হয় নাই। মসজিদে নববীতে উপস্থিত হইয়া সমবেত জনতার নিকট হইতে প্রকাশ্যভাবে অনুমতি লওয়ার পরই তিনি তাহা গ্রহণ করিতে সম্মত হইয়াছিলেন। পৃথিবীর বড়বড় শাসকদের ইতিহাস অনুরূপ কোন দৃষ্টান্ত পেশ করিতে পারে কি?
হযরত উমর ফারুক (রা) জনগণকে সমালোচনার অবাধ অধিকার প্রদান করিয়াছিলেন। ফলে একজন সাধারণ নাগরিকও খলীফার সমালোচনা করিতে বিন্দুমাত্র পরোয়া করিত না। কেবল পুরুষ নাগরিকগণই এই সুযোগ ভোগ করিতে পারিত তাহা নহে, নারী সমাজও এই ক্ষেত্রে কিছুমাত্র পাশ্চাদপদ ছিল না। স্ত্রীর মোহরানা নির্ধারণ বিষয়ে খলীফা মতের প্রতিবাদ করিয়া যখন একজন স্ত্রীলোক বলিয়া উঠিলঃ ‘হে উমর!আল্লাহ্র ভয় কর,’ তখন উমর ফারুক (রা)ও নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া তাহা পরিহার করেন এবং কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী উক্ত স্ত্রী লোকটির মত অঙ্কুন্ঠিত চিত্তে মানিয়া লইলেন। বস্তুতঃহযরত উমর (রা)-এর খিলাফতের অভূতপূর্ব সাফল্যের মূলে এই ধরণের ইনসাফ ও ন্যায়নীতিই কার্যকর রহিয়াছেন।
ফারুকী খিলাফতের আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা
হযরত উমর (রা) গোটা ইসলামী রাজ্যকে মোট আটটি প্রদেশে বিভক্ত করিয়া লইয়াছিলেন। মক্কা, মদীনা, সিরিয়া, বসরা, কুফা,মিসর ও ফিলিস্তিন। এই কয়টি এলাকা তখন সতন্ত্র ও ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ হিসাবে গণ্য হইত। এতদ্ব্যতীত খোরাসান,আযারবাইজান ও পারস্য এই তিনটি প্রদেশও তাঁহার খিলাফতের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। প্রতিটি প্রদেশের জন্য আলাদাভাবে গভর্নর, বেসামরিক ও সামরিক বিভাগের চীফ সেক্রেটারী, প্রধান কালেক্টর, পুলিশ বিভাগের ডিরেক্টর, প্রধান খাজাঞ্জী, প্রধান বিচারপতি প্রভৃতি উচ্চপদস্থ কর্মচারী নিযুক্ত করা হইয়াছিল।
সাধারণতঃমজলিসে শু’রার পরামর্শক্রমেই এই সব দায়িত্বপূর্ণ পদে লোক নিযুক্ত করা হইত। খলীফার প্রধান কাজ ছিল প্রদেশসমূহের শাসনকর্তাদের প্রতি তীক্ষ্ণ ও সতর্ক দৃষ্টি রাখা এবং তাঁহাদের স্বভাব-চরিত্র ও আদত-অভ্যাসকে ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে গড়িয়া তোলা। খলীফা উমর (রা) এই কাজ বিশেষ দক্ষতা সহকারেই সম্পন্ন করিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন ইসলামী রাষ্ট্রের এক অতন্দ্র প্রহরী। প্রশাসনে ইসলামী আদর্শের একবিন্দু বিচ্যুতি তিনি বরদাশত করিতে মাত্রই প্রস্তুত ছিলেন না। শাসনকর্তা ও দায়িত্বপূর্ণ পদে লোক নিয়োগের সময় তাঁহাদের নিকট হইতে তিনি এই প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিতেন যে তাঁহারা কঠোরভাবে ইসলামী আদর্শ মানিয়া চলিবেন এবং বিলাসিতা অথবা জাহেলী সভ্যতার কোন প্রভাবই কবুল করিবেন না। সেই সঙ্গে তাঁহাদের যাবতীয় ধন-সম্পদের একটি পূর্ণ তালিকাও তৈয়ার করিয়া লইতেন; উত্তরকালে কাহারো ধন-সম্পদে অস্বাভাবিক স্ফীতি পরিলক্ষিত হইলে পূর্বাহ্ণে রচিত তালিকার সহিত উহার তুলনা ও যাচাই করিয়া দেখিতেন। কাহারো সম্পত্তি অকারণে স্ফীত হইতে দেখিলে তাহার অর্ধেক পরিমাণ বায়তুলমালে ক্রোক করিয়া লইতেন।
শাসক ও পদস্থ অফিসারগণ যাহাতে কোথাও সীমানা লঙ্ঘন করিতে না পারে, সেদিকে খলীফা উমর (রা)-এর বিশেষ দৃষ্টি ছিল। এইজন্য তিনি প্রত্যেক হজ্জের সময়ই সাধারণভাবে ঘোষণা করিয়া দিতেন, কোন সরকারী কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কাহারো কোন অভিযোগ থাকিলে তাহা অনিতিবিলম্বে খলীফার গোচরীভূত করিতে হইবে। সেই সঙ্গে তিনি সকল অভিযোগের যথোচিত প্রতিকারেরও সুষ্ঠু ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন, যেন কোন অভিযোগ শুধু অভিযোগের পর্যায়েই থাকিয়া না যায়, বরং প্রতিটিরই যেন আশু প্রতিকার গ্রহণ করা হয়।
শাসকদের দ্বার জনগণের জন্য সর্বদা উন্মুক্ত রাখার জন্য খলীফাতুল মুসলিমীন বিশেষ তাকিদ করিতেন। জনগণের ফরিয়াদ শাসকদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করার পথে কোথাও বিন্দুমাত্র বাঁধার সৃষ্টি হইতে দেখিলে তিনি অবলিম্বে তাহা দূরীভূত করিয়া দিতেন। তিনি দায়িত্বশীল সরকারী কর্মচারীদিগকে দৈনন্দিন কর্তব্য পালনে সদা তৎপর থাকার জন্য সব সময় তাকীদ করিতে থাকিতেন। এই পর্যায়ে হযরত আবূ মূসা আশয়ারী(রা) কে যে উপদেশ পাঠাইয়াছিলেন, তাহা সর্বকালের সর্বদেশের সরকারী কর্মচারীদের জন্য মহামূল্য দিক-নির্দেশনারূপে গণ্য হইবে। তিনি লিখিয়াছিলেনঃ
*******(আরবী)
অতঃপর জানিবে, সুষ্ঠু কর্মপন্থা এই যে, অদ্যকার কাজ আগামী কালের জন্য ফেলিয়া রাখিবে না। এইরূপ করিলে তোমাদের নিকট অনেক কাজ জমিয়া যাইবে। ফলে কাজের চাপে তুমি দিশাহারা হইয়া পড়িবে। কি করিবে, কোনটা করিবে, কোনটা করিবে না, তাহার দিশা পাইবে না। পরিনামে সব কাজই বিনষ্ট করিয়া ফেলিবে।
জনগণের নৈতিক মান সংরক্ষণ
শাসকদের ছাড়াও ইসলামী রাষ্ট্রের অধিবাসী সাধারণ জনগণের নৈতিক চরিত্র ও ধর্মীয় মর্যাদা সংরক্ষণের জন্য খলীফা বিশেষ দায়িত্ব সহকারে অবিরাম কাজ করিতেন। বস্তুত তিনি নিজে যেরূপ ইসলামী নৈতিকতার বাস্তব প্রতীক ছিলেন, সমষ্টিগতভাবে গোটা মুসলিম জাতিকে এবং ব্যক্তিগতভাবে প্রতিটি মুসলিমকে অনুরূপ গড়িয়া তোলার জন্য তিনি আপ্রাণ চালাইয়া যাইতেন। তৎকালে বংশীয় আভিজাত্যের ঐতিহিক গৌরব এবং ব্যক্তিগত অহংকার আরবদের হাড়ে-মজ্জায় মিশ্রিত ছিল, মনীব ও নওকরের মাঝে ছিল মানুষ-অমানুষের পার্থক্য। কিন্তু দ্বিতীয় খলীফা ইসলামী শিক্ষা ও নৈতিক ভাবধারার গতি-প্রবাহে এইসবের কলংক ও আবর্জনারাশি ধুইয়া-মুছিয়া নিঃশেষ করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি নিজে খাদ্য গ্রহণকালে ফকীর-মিসকিন ও ক্রীতদাসদের নিজের সঙ্গে বসাইয়া খাওইতেন। তিনি বলিয়াছেনঃ ‘ক্রীতদাস ও ফকীর-মিসকীনের সঙ্গে একত্রে আহার করাকে যাহারা লজ্জাকর ও মর্যাদাহানিকর মনে করে, তাহাদের উপর আল্লাহ্র অভিশাপ’। বস্তুত দুনিয়ার ইতিহাসে আজ পর্যন্ত এইরূপ সাম্যবাদী শাসকের অন্য কোন দৃষ্টান্ত খুঁজিয়া পাওয়া যাইতে পারে না।
তৎকালীন সমাজের লোকদের উপর কবি ও কবিতার খুব প্রভাব ছিল। যেসব কবি লোকদের প্রতি অশ্লীল গালাগালমূলক কবিতা রচনা করিত, রাষ্ট্রীয় ফরমান প্রচার করিয়া খলীফা উমর (রা) সেসব বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন।লোকদের পরস্পরের মধ্যে হিংসা ও বিদ্বেষাগ্নি দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া মুসলিম ভ্রাতৃত্বের সুদৃঢ় প্রাসাদকে যাহাতে ভস্ম করিয়া দিতে না পারে এবং জনসাধারণ যাহাতে জাতীয় লক্ষ্য ও আদর্শ ভুলিয়া গিয়া আয়েশ-আরাম, জাঁকজমক, বিলাসিতা ও ভোগ-সম্ভোগে লিপ্ত হইয়া না পড়ে, সেদিকে তাঁহার বিশেষ নজর ছিল।
মোটকথা, মুসলমানদিগকে সকল প্রকার নৈতিক পতনের হাত হইতে রক্ষা করিয়া তাহাদিগকে উন্নত নৈতিক চরিত্রে ভূষিত করার জন্য তিনি বিশেষ যত্ন গ্রহন করিয়াছিলেন। সমাজের লোকদের মধ্যে পরিপূর্ণ সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব স্থাপন, তাহাদের মধ্যে আত্মসম্মানবোধ ও দায়িত্বজ্ঞান জাগ্রত করার জন্য তিনি কখনো চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। প্রাদেশিক শাসনকর্তাদিগকেও এ সম্পর্কে সর্বদা সতর্ক করিয়া রাখিতে চেষ্টা করিতেন।
আভ্যন্তরীণ শাসন-শৃঙ্খলা ব্যবস্থা
সিরিয়া ও ইরান দখলে আসার পর পর বিজিত অঞ্চলের কৃষি-জমি বিজয়ী সেনানীদের মধ্যে বণ্টন করার দাবি উঠিলে খলীফা তাহা অস্বীকার করেন। মজলিসে শুরার অধিবেশনে বিস্তারিত আলোচনার পর উমর ফারুক (রা)-এর মতের অনুকূলেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।
ফারুকী খিলাফতের আমলেই ইরাকের বিরাট এলাকার জরিপ গ্রহণ করা হয় সেখানকার চাষোপযোগী সমস্ত জমি জনসাধারণের মধ্যে বণ্টন করা হয়। তাহাদের নিকট হইতে উশর ও খারাজ আদায়ের ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। সিরিয়া ও মিসরে রাজস্ব আদায় শুরু করা হয়। ব্যবসায় শুল্ক(duty tax) আদায় করা খলীফা উমর ফারুক (রা)-এর একটি ইজতিহাদী ফয়সালা এবং ইসলামী রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় তাঁহার আমলেই সর্বপ্রথম ইহার সূচনা হয়। বলাবাহুল্য, ইহা ইসলামের অর্থ-বিজ্ঞানের সহিত পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল।
দ্বিতীয় খলীফা সমগ্র মুসলিম জাহানের আদমশুমারী গ্রহণ করেন। তাঁহার আমলে জিলাসমূহে রীতিমত আদালত ও ফৌজদারী কোর্ট স্থাপিত হয়। বিচার বিভাগের জন্য প্রয়োজনীয় নিয়ম-কানুন নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়। বিচারকদের জন্য উচ্চহারে বেতন নির্ধারণ করা হয়, যেন ঘুষ-রিসওয়াতের প্রশ্রয় দেওয়ার বিন্দুমাত্র কারণ না ঘটে। ইহা ছাড়া বিভিন্ন জটিল বিষয়ের মীমাংসার জন্য তখন ফতোয়া বিভাগও খোলা হয়।
দেশের আভ্যন্তরীণ শান্তি ও নিরাপত্তা বিধানের জন্য তিনি পুলিশ বিভাগ স্থাপন করেন। হযরত আবূ বকর (রা)-কে বাহরাইনের সর্বোচ্চ পুলিশ কর্মচারী নিযুক্ত করিয়া পাঠাইবার সময় তাঁহাকে শান্তি ও নিরাপত্তা বিধানের সঙ্গে সঙ্গে জনগণের নৈতিক চরিত্রের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখার জন্য তিনি বিশেষ নির্দেশ দিয়াছিলেন। দোকানদারগণ যেন পরিমাপ ও ওজনের দিক দিয়া ক্রেতাকে বিন্দুমাত্র ঠকাইতে না পারে, রাজপথের উপর যেন কেহ ঘর-বাড়ি নির্মাণ না করে, ভারবাহী জন্তুর উপর দুর্বহ কোন বোঝা যেন চাপানো না হয় এবং শরাব উৎপাদন ও ক্রয়-বিক্রয় হইতে না পারে, সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবার জন্য পুলিশ বাহিনীকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। বস্তুত জনস্বার্থ ও শরীয়াতের নির্দেশ যাহাতে কিছুমাত্র ব্যাহত হইতে না পারে, বরং উভয়েরই মর্যাদা পুরাপুরি রক্ষা পাইতে পারে সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখাই ছিল পুলিশের মৌলিক দায়িত্ব।
ফারুকে আযম (রা)-এর পূর্বে আরব জাহানে কারাগারের কোন অস্তিত্ব ছিল না। তিনিই প্রথমবার মক্কা শরীফে কারাগার স্থাপন করেন। উত্তরকালে জিলাসমূহে কেন্দ্র-স্থলেও অনুরূপ কারাগার স্থাপন করা হয়।
বায়তুলমাল প্রতিষ্ঠা
ফারুকী খিলাফতের পূর্বে সরকারী ধন-সম্পদ সঞ্চিত রাখার কোন স্থায়ী প্রতিষ্ঠান বর্তমান ছিল না। যাহাকিছুই আমদানী হইত, সঙ্গে সঙ্গে তাহা প্রয়োজনীয় কাজে কিংবা অভাবগ্রস্তদের সাহায্যার্থে ব্যয় হইয়া যাইত। হযরত আবূ বকর (রা) যদিও একখানি ঘর বায়তুলমাল কায়েমের জন্য নির্দিষ্ট করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহা প্রায় সবসময় বন্ধ থাকিত; তাহাতে সঞ্চয় করিয়া রাখার মত কোন সম্পদই তখন ছিল না। তাঁহার ইন্তেকালের সময় বায়তুলমালে তল্লাসী চালানো হইতে উহাতে একটি মাত্র মুদ্রা অবশিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। হযরত উমর (রা) সম্ভবতঃ ১৫হিজরী সনে সর্বপ্রথম বায়তুলমাল প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন ও মজলিসে শু’রার মঞ্জুরীক্রমে মদীনা শরীফে বিরাটাকারে বায়তুলমাল প্রাসাদ নির্মাণ করেন। রাজধানীতে বায়তুলমাল প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর জিলা কেন্দ্রসমূহেও অনুরূপ বায়তুলমাল প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রতিটি স্থানেই এই বিভাগের জন্য সতন্ত্র অফিসার নিযুক্ত করা হয়। শাখা বায়তুলমালসমূহের বার্ষিক আয় হইতে স্থানীয় খরচ নির্বাহ করার পর যাহাকিছু উদ্ধৃত্ত থাকিত, তাহা কেন্দ্রিয় বায়তুলমালে-মদীনা তাইয়্যেবায়-প্রেরণ করা হইত। বায়তুলমালের দায়িত্ব ও ব্যয়ভার সম্পর্কে সঠিক অনুমান করার জন্য এই কয়টি কথাই যথেষ্ট যে, রাজধানীর অধিবাসীদের জন্য যে বেতন ও বৃত্তি নির্দিষ্ট ছিল, তাহার পরিমাণই ছিল তিন কোটি দিরহাম। বায়তুলমালের হিসাব রক্ষার জন্য সতন্ত্র বিভাগ ও হিসাবের বিভিন্ন জরুরী খাতাপত্রও যথাযথভাবে চালু করা হইয়াছিল। আরবে তখনো সুষ্ঠুভাবে কোন বৎসর গণনা প্রচলিত ছিল না; হযরত উমর ফারুক (রা) ১৬ হিজরীতে হিজরী সনের হিসাব চালু করিয়া এই অভাব পূরন করিয়া দেন।
গৃহ নির্মাণ ও পূর্তবিভাগীয় কাজ
ইসলামী রাষ্ট্রের পরিধি যতই বিশাল আকার ধারণ করিতে থাকে, বিভিন্ন দালান-কোঠা নির্মাণের কাজ ততই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। হযরত উমর (রা)-এর শাসনামলে এই কার্য সম্পাদনের জন্য স্বতন্ত্র কোন বিভাগ ছিল না। তাহা সত্ত্বেও প্রাদেশিক শাসনকর্তা ও উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের দায়িত্বে এই কাজ সুষ্ঠুরূপে অগ্রসর হইতে থাকে। প্রতিটি স্থানেই অফিসারদের বসবাসের জন্য সরকারী দালান-কোঠা ও জনগণের সুখ-সুবিধার জন্য পুল, সড়ক ও মসজিদ নির্মিত হয়। অনুরূপভাবে সামরিক প্রয়োজনে দুর্গ, ক্যাম্প ও বারাকসমূহ নির্মাণ করা হয় এবং রাজকোষের হেফাজতের জন্য বায়তুলমাল বা খাজাঞ্জীখানার দালান তৈয়ার করা হয়। রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে হযরত উমর (রা)-এর ব্যয়-সংকোচন নীতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাহা সত্ত্বেও বায়তুলমালের প্রাসাদ সাধারণতঃ বেশী মজবুত ও জাঁকালভাবে তৈয়ার করা হয়।
মক্কা ও মদীনার মধ্যে বিশেষ সম্পর্কের কারণে উভয় শহরের যোগাযোগ ও যাতায়াত ব্যবস্থা অত্যন্ত সুগম ও শান্তিপূর্ণ হওয়া আবশ্যক ছিল। হযরত উমর (রা) মদীনা হইতে মক্কা পর্যন্ত দীর্ঘ পথের পার্শ্বে অনেকগুলি পুলিশী পাহারা, সরাইখানা ও ঝর্ণাধারা নির্মাণ করেন।
কৃষিব্যবস্থার উন্নয়ন ও উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য খলীফা সমগ্র দেশে কূপ বা খাল খনন করিয়া সেচকার্য সম্পাদনের সুষ্ঠু ব্যবস্থা করিয়া দেন। বসরায় মিষ্টি পানি সরবরাহের উদ্দেশ্যে দজলা নদী হইতে খাল খনন করা হয়। এই খালের দৈর্ঘ্য ছিল প্রায় নয় মাইল।এই প্রসঙ্গে নহরে মা’কাল, নহরে মায়াদ ও নহরে আমীরুল মু’মিনীন-এর কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।
শহর নির্মাণ
আরবের উষর-ধূষ্র মরুভূমির বুক হইতে বিশ্ব-বিজয়ী শক্তি হিসাবে মুসলিমগণ যখন বহির্বিশ্বে পদার্পণ করিল, তখন অন্যান্য দেশের সবুজ-শ্যামল ও মনোরম দৃশ্য তাহাদিগকে মুগ্ধ করে। ইসলামী আদর্শ প্রচার ও প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব পালনের জন্য ইসলামী রাষ্ট্রের তরফ হইতে বিভিন্ন সরকারী কার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে তাহারা রাজধানী মদীনা হইতে বহু দূর দূরাঞ্চলে বসবাস অবলম্বন করিতে বাধ্য হয়। ইহার ফলে তাহাদের দ্বারা প্রতিবেশী দেশসমূহ বিভিন্ন শহর ও নগর গড়িয়া উঠে। হযরত উমর ফারুক (রা)-এর খিলাফত কালে বসরা,কুফা, ফুস্তাত, মুসেল প্রভৃতি ইতিহাস-বিখ্যাত নগরসমূহ স্থাপিত হয়। বসরা শহরে প্রথমে মাত্র আটশত লোক বসবাস শুরু করে; পরে অল্পদিনের মধ্যেই অধিবাসীদের সংখ্যা প্রায় এক লক্ষ বিশ হাজার পর্যন্ত পৌঁছে। ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্র হিসাবে এই শহর শতাব্দী কাল পর্যন্ত মুসলমানদের গৌরবের বস্তু হইয়া থাকে। ইরাকের জৈনক আরব শাসনকর্তা রাজধানী পুনঃনির্মাণ করায় কুফা নগরের সৃষ্টি হয়। এই শহরে চল্লিশ হাজার লোকের বাসোপযোগী গৃহাদি নির্মাণ করা হয়। হযরত উমর (রা)-এর নির্দেশক্রমে ইহার সড়কসমূহ চল্লিশ হাত প্রশস্ত করিয়া তৈয়ার করা হয়। এখানে যে জামে মসজিদ নির্মিত হয়, তাহাতে এক সঙ্গে চল্লিশ হাজার মুসলমান নামায আদায় করিতে পারে। জ্ঞান-বিজ্ঞান-কেন্দ্র হিসাবে এই শহরের ঐতিহাসিক মর্যাদা সর্বজনবিদিত।
ফুস্তাত শহর নির্মাণের ইতিহাস অত্যন্ত মর্মস্পর্শী। মিসর বিজয়ী হযরত আমর ইবনুল আস (রা) নীল দরিয়া ও মাকতাম পর্বতের মধ্যবর্তী স্থানে সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করেন। এই সময় ঘটনাবশতঃএকটি কবুতর তাঁহার তাঁবুতে নীড় রচনা করে। হযরত আমর (রা) যখন এই স্থান ত্যাগ করিয়া যাইতেছিলেন, তখন এই আসমানী অতিথির শান্ত-নীড় জীবনে যেন কোনরূপ ব্যাঘাত সৃষ্টি না হয় সেই চিন্তায় তিনি তাঁবুকে যথাযথভাবে দাঁড় করিয়া রাখিলেন। উত্তরকালে এই তাঁবুকে কেন্দ্র করিয়াই ফুস্তাত শহর গড়িয়া উঠে। চতুর্থ শতাব্দীর জৈনক পর্যটক এই শহর সম্পর্কে লিখিয়াছেনঃ
এই শহর বাগদাদের প্রতিদ্বন্দ্বী পাশ্চাত্যের কেন্দ্র ও ইসলামের গৌরব। এখানকার জামে মসজিদ অপেক্ষা মুসলিম জাহানের আর কোন মসজিদে জ্ঞান-বিজ্ঞান আলোচনার এতো বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় না। এখানকার সামুদ্রিক বন্দরে দুনিয়ার অধিক সংখ্যক জাহাজ নোঙর করিয়া থাকে।
মুসেল শহর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যর সংগমস্থলে অবস্থিত; এই দৃষ্টিতেই সম্পূর্ণ গ্রামীণ পরিবেশে নির্মিত এই শহরের নামকরণ হইয়াছে। ইহা একটি অজ পাড়াগাঁকে বিরাট শহরে পরিণত করার এক বাস্তব নিদর্শন। হযরত উমর (রা)-এর নির্দেশে এখানে একটি বিশাল জামে মসজিদ নির্মাণ করা হয়। আলেকজান্দ্রিয়া বিজয়ের পর হযরত আমর ইবনুল আস(রা) সমুদ্রোপকূলে কিছু সংখ্যক সৈন্য রাখিয়া দেন। কেননা সমুদ্র-পথে রোমান শত্রুদের আক্রমণের ভয় ছিল। উত্তরকালে এখানে একটি বিরাট উপনিবেশ গড়িয়া উঠে।
সামরিক ব্যবস্থাপনা
ইসলাম যখন রোমান সাম্রাজ্য অপেক্ষাও অধিক বিশাল রাজ্যের মালিক হইয়া বসিল এবং কাইসার ও কিসরার বিশাল বিস্তীর্ণ রাজ্যসমূহ উহার অধিকারভুক্ত হইল, তখন একটি সুসংবদ্ধ সামরিক ব্যবস্থাপনা উহার জন্য অপরিহার্য হইয়া পড়ে। হযরত উমর (রা) ১৫ হিজরী সনে ে সম্পর্কে কার্যকর নীতি অবলম্বন করেন এবং সমগ্র মুসলিম জাহানকে সামরিক জাতি রূপে গড়িয়া তোলার চেষ্টা শুরু করে। প্রথম পর্যায়ে আনসার ও মুহাজির মুসলমানদিগকে লইয়া কাজ আরম্ভ করা হয়। তাহাদের প্রত্যেকের জন্য মর্যাদানুপাতে বেতন ধার্য করা হয়। এই ব্যাপারে বিশেষ লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, যাহাদের জন্য যত পরিমাণ বেতন ধার্য করা হয়, তাহাদের ক্রীতদাসদের জন্যও সম পরিমাণ বৃত্তি নির্দিষ্ট করা হয়।
কিছুদিন পর এই নীতি আরো অধিক ব্যাপক আকারে ধারণ করে। আরবের সমগ্র গোত্র ও কবীলার লোকদিগকেও ইহার অন্তর্ভুক্ত করিয়া লওয়া হয়। শেষ পর্যন্ত দুগ্ধপোষ্য শিশুদের জন্যও বৃত্তি নির্ধারণ করা হয়। ইহার অর্থ এই ছিল যে, আরবের জাহানের প্রতিটি শিশুকে জন্মদিন হইতেই ইসলামী সৈন্যবাহিনীর একজন সিপাহীরুপে গণ্য করা হইল।
সৈনিকদিগকে বিশেষভাবে ট্রেনিং দানের দিকে হযরত উমর (রা)-এর সতর্ক দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল; এমনকি বিজিত এলাকাসমূহের কেহ যেন সামরিক জীবন পরিত্যাগ করিয়া কৃষিকার্য ও ব্যবসায়-বাণিজ্যে লিপ্ত হইয়া না পড়ে, সে জন্য বিশেষ তাকীদী ফরমান প্রচার করা হইয়াছিল। কেননা তাহা করা হইলে মুসলিম মুজাহিদদের সামরিক যোগ্যতা প্রতিভা, বীরত্ব ও সাহসিকতা বিলুপ্ত হইয়া যাওয়ার সমূহ আশংকা ছিল।
দ্বিতীয় খলীফার আমলে সৈনিকদের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য বিশেষ যত্ন লওয়া হইত; সৈনিকদের ক্যাম্প তৈয়ার করার ব্যাপারে আবহাওয়ার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা হইত। বসন্তকালে সৈনিকদের সবুজ-শ্যামল অঞ্চলে প্রেরণ করা হইত। প্রায় সকল বড় বড় শহরের উপকণ্ঠে সামরিক কেন্দ্র স্থাপন করা হইয়াছিল। শত্রু শিবির হইতে গোপন সংবাদ সংগ্রহের জন্য সামরিক গোয়েন্দা বিভাগকে বিশেষ তৎপর করিয়া তোলা হইয়াছিল। বস্তুতঃহযরত উমর ফারুক (রা) তেরোশত বৎসর পূর্বে যে সামরিক রীতি-নীতি নির্ধারণ করিয়াছিলেন, মূল-নীতির দিক দিয়া প্রায় দেড় হাজার বৎসর পরও তাহাতে কিছুমাত্র রদ-বদল হওয়াতো দূরের কথা, তাহাতে কিছু পরিবর্ধন করাও আজ পর্যন্ত সম্ভব হয় নাই। আরবদের শানিত তরবারি বিজয় লাভের ব্যাপারে কখনো অপর কাহারো অনুগ্রহভাজন হইতে প্রস্তুত হয় নাই; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও শত্রুপক্ষকে তাহাদেরই স্বগোত্রীয় জাতিসমূহের সহিত সংগ্রামে লিপ্ত করিয়া দেওয়া সমর কৌশলের একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি বলিয়া হযরত উমর (রা) বিশেষ কৃতিত্ব সহকারেই এই রণকৌশল কার্যকর করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ফলে অনারব, রোমান ও গ্রীক জাতির অসংখ্য বীর-যোদ্ধা ইসলামী সৈন্যবাহিনীতে শামিল হইয়া নিজ নিজ জাতির লোকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছেন, ইতিহাসে ইহা চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিব।
ইসলামের প্রচারের কাজ
হযরত উমর ফারুক (রা) ধর্ম-প্রচার ও প্রতিষ্ঠার কাজ বিশেষ মনোযোগ সহকারেই সম্পন্ন করিতেন। লোকদিগকে ইসলামে দীক্ষিত করার ব্যাপারে তিনি কখনো তরবারি কিংবা রাষ্ট্র-শক্তি প্রয়োগ করেন নাই; বরং ইসলামী জীবনাদর্শের বৈশিষ্ট্য, ইহার অতুলনীয় সৌন্দর্য এবং অন্তর্নিহিত মর্মস্পর্শী ভাবধারায় মুগ্ধ ও আকৃষ্ট করিয়াই তিনি লোকদিগকে মুসলিম বানাইতে চেষ্টা করিতেন। তিনি তাঁহার ক্রীতদাসকে ইসলাম কবুল করার আহ্বান জানাইলে উহা গ্রহণ করিতে সে স্পষ্ট ভাষায় অস্বীকার করে। তখন তিনি বলিলেন ‘লা-ইকরাহা ফিদ্বীন’- ‘দ্বীন ইসলাম কবুল করার ব্যাপারে কোন জোর-জবরদস্তি করা যাইতে পারে না’।
কাফিরের সহিত সংগ্রাম ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া শেষবারের তরে ও সর্বশেষ সুযোগ হিসাবে তিনি ইসলাম কবুল করার দাওয়াত পেশ করিয়াছেন। কেননা ঠিক সেই মুহূর্তেও কেহ ইসলাম কবুল করিলে তাদের সহিত যুদ্ধ করা হারাম হইয়া যায়। যুদ্ধ ও রক্তপাত পরিহার করার জন্য ইহা ছিল মুসলমানদের শেষ প্রচেষ্টা। হযরত উমর (রা) সমগ্র মুসলমানকে ইসলামী নৈতিকতার জীবন্ত প্রতীকরূপে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। ফলে যে পথ ও জনপদের উপর হইতেই তাহারা অগ্রসর হইত, সেখানেই তাহাদের নৈতিক-চরিত্র ও মধুর ব্যবহারের প্রভাব প্রতিফলিত হইত এবং সত্য-সন্ধ জনতা তাহাতে মুগ্ধ ও বিমোহিত হইয়া ইসলামে দীক্ষিত হইত। রোমান সম্রাটের রাষ্ট্রদূত ইসলামী সৈন্য-কেন্দ্রে আগমন করিলে সেনাপতির সরল জীবন-যাত্রা, অকপটতা ও উদার ব্যবহার দেখিতে পাইয়া স্বতঃস্ফূর্তভাবে ইসলাম গ্রহণ করেন। মিসরের জনৈক প্রভাশালী ব্যক্তি মুসলমানদের বৈশিষ্ট্যের সাথে লোকমুখে শুনিতে পাইয়া এতদূর মুগ্ধ হন যে, দুই সহস্র জনতাসহ অনতিবিলম্বে ইসলাম কবুল করেন।
ইসলাম প্রচারের পর সর্বাপেক্ষা জরুরী কাজ ছিল স্বয়ং মুসলমানদিগকে ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া তোলা ও ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতির বাস্তব প্রতিষ্ঠা করা। এই পর্যায়ে হযরত উমর (রা)-এর প্রচেষ্টা প্রথম খলীফার আমল হইতেই বিশেষভাবে শুরু হইয়াছিল। ইসলামের উৎস ও একমাত্র মূলসূত্র কুরআন মজীদ গ্রন্থাকারে প্রকাশ করার মূলে উমর ফারুক (রা)-এর প্রচেষ্টা সর্বজনবিদিত। খলীফা হইয়া তিনি পূর্ণ শক্তিতে উহার ব্যাপক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন। এই উদ্দেশ্যে নিযুক্ত শিক্ষকদিগের জন্য সম্মানজনক বেতন নির্ধারণ করা হয়। সিরিয়ার কয়েকজন বিশিষ্ট সাহাবিকে কুরআন শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হয়। কুরআন মজীদকে পূর্ণ বিশুদ্ধ ও নির্ভুলরূপে অধ্যয়ন করার জন্য চতুর্দিকে ব্যাপকভাবে কুরআন চর্চা শুরু হইয়া যায়।
ইসলামী জীবন-ব্যবস্থায় কুরআনের পরই হইতেছে হাদীসের স্থান। হাদীসের খেদমত করার ব্যাপারেও হযরত উমর ফারুক (রা)-এর আন্তরিক প্রচেষ্টার অন্ত ছিল না। তিনি নবী করীম (স)-এর বহু সংখ্যক হাদীস লিপিবদ্ধ করিয়া প্রদেশসমূহের শাসনকর্তাদের নামে পাঠাইয়াছিলেন এবং সাধারণ্যে তাহা প্রচার করার নির্দেশ দিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া বিভিন্ন সাহাবীকে হাদীস শিক্ষাদানের জন্য কুফা,বসরা ও সিরিয়া প্রভৃতি এলাকায় তিনি প্রেরণ করিয়াছিলেন।
হযরত উমর ফারুক (রা) অবশ্য হাদীস গ্রহণের ব্যাপারে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতেন। কেননা মুহাদ্দিসদের দৃষ্টিতে সকল সাহাবীই বিশস্ত ও নির্ভরযোগ্য হইলেও তাঁহারা কেহই মানবীয় বৈশিষ্ট্য ও গুনাগুণের ঊর্ধ্বে ছিলেন না, একথা তিনি খুব ভালো করিয়া জানিতেন। এই কারণে তিনি বেশী পরিমাণে হাদীস বর্ণনা করা সম্পর্কে লোকদিগকে বিশেষভাবে সতর্ক করিয়া দেন এবং লোকেরা যাহাতে প্রথমেই কুরআনের দিকে লক্ষ্য আরোপ করে এবং ইহার পর হাদীস গ্রহন করে, সেজন্য তিনি সংশ্লিষ্ট সকলকেই সতর্ক করিয়া দেন।
হাদীসের পরই হইতেছে ফিকাহর স্থান। খলীফা উমর (রা) নিজেই বিভিন্ন খোতবা প্রসঙ্গে ফিকাহর মসলা-মাসায়েল বর্ণনা করিতেন এবং দূরবর্তী স্থানের শাসকদের নামেও ফিকাহর জরুরী মুসলাসমূহ সময় সময় লিখিয়া পাঠাইতেন। যে সব বিষয়ে মতবৈষম্যের সৃষ্টি হইত, তাহা সাহাবীদের প্রকাশ্য মজলিসে তিনি পেশ করিতেন ও যথাসম্ভব সর্বসম্মতভাবে মিমাংসা করিয়া লইতেন। জিলার পদস্থ কর্মচারী নিয়োগের ব্যাপারে লোকদের ইসলামী বিধান ও আইন-কানুন সম্পর্কিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার দিকে তিনি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতেন এবং সমগ্র মুসলিম জাহানে ইসলামী আইনের ব্যাপক প্রচারের জন্য ফিকাহবিদগণকে উচ্চমানের বেতনে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সংক্ষেপ কথা এই যে, দ্বিতীয় খলীফার শাসন আমলে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের ব্যাপক শিক্ষা ও প্রচারের সুষ্ঠু ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। দ্বিতীয় খলীফার আমলে সমগ্র এলাকায় মসজিদ নির্মাণ এবং তাহাতে ইমাম মুহাযযিন নিযুক্ত করা হয়। লোকদের সুবিধার্থে হেরেম শরীফ অধিক প্রশস্ত করিয়া দেওয়া হয়। মসজিদে নববীকেও অনেক বড় করিয়া তৈয়ার করা হয়। তিনি প্রত্যেক বৎসরই নিজে হজ্জে গমন করিতেন ও হাজীদের যাবতীয় সুখ-সুবিধা বিধানের দিকে নিজেই লক্ষ্য রাখিতেন।
সাধারণ জনকল্যাণমূলক কাজ
১৮ হিজরীতে আরবদেশে যখন সর্বগ্রাসী দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, তখন হযরত উমর (রা) গভীরভাবে উদ্বিগ্ন,সন্ত্রস্ত ও বিচলিত হইয়া পড়েন। তিনি নিজে এই সময় সকল প্রকার সুখ-সম্ভোগ, আরাম-আয়েশ ও চর্ব্য-চোষ্য-লেহ্য পেয়র স্বাদ আস্বাদন পরিহার করেন। তাঁহার নিজের পুত্রকে ফল খাইতে দেখিয়া খলীফা ক্রুদ্ধঃহইয়া বলিলেনঃ ‘সমগ্র দেশবাসী বুভুক্ষু, ক্ষুধার যন্ত্রণায় ছটফট করিতেছে আর তুমি সুমিষ্ট ও পুষ্টিকর ফলের স্বাদ গ্রহন করিতেছ? এই সময় জনগণের দুঃখ-কষ্ট লাঘব করার জন্য তিনি যে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন,ইতিহাসে তাহা চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। এই সময় বায়তুলমালের সমস্ত ধন-সম্পদ তিনি অকুণ্ঠিত চিত্তে ব্যয় করেন এবং চারিদকে হইতে খাদ্য আমদানী করিয়া দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িতদের মধ্যে বণ্টন করেন। তিনি লা-ওয়ারিস শিশুদিগকে দুগ্ধ-পান ও লালন-পালন করার সুষ্ঠু ব্যবস্থা করেন এবং গরীব-মিসকীনদের জন্য জীবিকার সংস্থান করেন। তবে তাহার এই ব্যবস্থা সাধারণভাবে সকল গরীব ও মিসকীনদের জন্য ছিল না, বিশেষভাবে যাহারা উপার্জনে অক্ষম ছিল, তাহাদের জন্যই ছিল এই ব্যবস্থা।
হযরত উমর (রা)-এর আশ্চার্যজনক কর্মনীতি এই ছিলে যে, তিনি আঙ্গুর ফসলের উপর অতিরিক্ত কর ধার্য করিতেন এই জন্য যে, তাহা ছিল তখনকার যুগে একমাত্র ধনীদের খাদ্য আর খেজুরের উপর অপেক্ষাকৃত কম কর ধার্য করিতেন; কেননা তাহা ছিল অপেক্ষাকৃত গরীব ও সাধারণ জনগণের খাদ্য।
দেশের দূরবর্তী এলাকাসমূহের আভ্যন্তরীণ খুঁটিনাটি অবস্থা সম্পর্কেও হযরত উমর (রা) বিশেষভাবে অবহিত থাকিতেন এবং কোন কিছুই তাঁহার অজ্ঞাত ও দৃষ্টির অগোচর থাকিতে পারিত না। এমন কি, লোকদের পারিবারিক জীবনের বদ্ধ পরিবেশেও কোন প্রকার শরিয়াত-বিরোধী অনাচারের সৃষ্টি হইলে অথবা কেহ অভাব-দারিদ্রের নিষ্ঠুর আঘাতে জর্জরিত হইয়া থাকিলে তাহাও খলীফা উমর ফারুক (রা)-এর অজ্ঞাত থাকিয়া যাইত না। এইজন্য তিনি সমগ্র দেশে রিপোর্টার ও বিবরণকারী লোক নিযুক্ত করেন। ঐতিহাসিক তাবারী লিখিয়াছেনঃ
******(আরবী)
উমর ফারুক (রা) কোন বিষয়েই অনবহিত থাকিতেন না। ইরাকে যাহারা বিদ্রোহ করিয়াছিল এবং সিরিয়ায় যাহাদিগকে পুরস্কৃত করা হইয়াছিল, সেইসব কিছুর বিস্তৃত বিবরণ তাঁহাকে লিখিয়া পাঠান হইয়াছিল।
হযরত উমর (রা)-এর গোয়েন্দা বিভাগ এক শাসনকর্তা গোপন বিলাস জীবনের বিবরণ তাহার এক পত্রের মাধ্যমে জানিতে পারে। খলীফা এই বিষয়ে অবহিত হইয়া তাহাকে পদচ্যুত করেন এবং লেখেন যে, তোমার বর্তমান জীবন ধারণ আমি সহ্য করিতে পারি না।
বিচার ইনসাফ
ফারুকী খিলাফতের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য দিক তাঁহার নিরপেক্ষ, সুবিচার ও পক্ষপাতহীন ইনসাফ। তাঁহার শাসন আমলে এক বিন্দু পরিমাণ না-ইনসাফীও অনুষ্ঠিত হইতে পারিত না।
ফারুকে আযম (রা)-এর এই ঐতিহাসিক বিচার-ইনসাফ কেবল মুসলমান পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিল না, তাঁহার সুবিচারের দ্বার ইয়াহুদী,খৃস্টান,মাজুসী প্রভৃতি অমুসলিম নাগরিকদের জন্যও অবারিত ও চির-উন্মুক্ত ছিল। হযরত উমর (রা) জনৈক অমুসলিম বৃদ্ধ ব্যক্তিকে ভিক্ষা করিতে দেখিয়া ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে উত্তরে সে বলিলঃ ‘আমার উপর ‘জিজিয়া’ ধার্য করা হইয়াছে, অথচ আমি একজন গরীব মানুষ’। হযরত উমর (রা) তাহাকে নিজের ঘরে লইয়া গেলেন ও কিছু নগদ সাহায্য করিলেন এবং বায়তুলমালের ভারপ্রাপ্তকে লিখিলেনঃ ‘এই ধরণের আরও যত ‘যিম্মী’ গরীব লোক রহিয়াছে, তাহাদের সকলের জন্য বৃত্তি নির্দিষ্ট করিয়া দাও। আল্লাহ্র কসম, ইহাদের যৌবনকাল কাজ আদায় করিয়া বার্ধক্যে ইহাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা না করা কিছুতেই ইনসাফ হইতে পারে না’। বস্তুত দুনিয়ার মানুষের দুঃখ মোচনের জন্য উমর ফারুক (রা)-এর খিলাফত চিরদিনের জন্য এক উজ্জ্বল আদর্শ।
হযরত উসমান (রা)- এর চরিত্র বৈশিষ্ট্য
হযরত উসমান (রা) খিলাফতে রাশেদা’র তৃতীয় খলীফা। তাঁহার ব্যক্তিগত চরিত্রে ‘খলীফায়ে রাশেদ’ হওয়ার সব বৈশিষ্ট্যই পূর্ণ মাত্রায় বর্তমান ছিল। তিনি স্বভাবতঃই পবিত্রচরিত্র,বিশ্বাসপরায়ণ,সত্যবাদী, ন্যায়নিষ্ঠ, সহনশীল এবং দরিদ্র-সহায় ছিলেন। জাহিলিয়াহ যুগের ঘোরতর মদ্যপায়ী সমাজে বসবাস করা সত্ত্বেও মদ্য ছিল তাঁহার অনাস্বাদিত। রাসূলে করীম (স)-এর পবিত্র সাহচর্য তাঁহার নৈতিক চরিত্রকে অধিকতর নির্মল,পরিচ্ছন্ন ও দীপ্তিমান করিয়া তুলিয়াছিল।
বস্তুত আল্লাহ্র ভয়ই নৈতিক চরিত্রের মূল উৎস। যাঁহার দিল আল্লাহ্র ভয়ে ভীত-কম্পিত নয়, সে না করিতে পারে হেন পাপ কার্যের উল্লেখ করা যায় না। হযরত উসমান (র) আল্লাহ্র ভয়ে সর্বদা কম্পিত ও অশ্রুসিক্ত থাকিতেন। কবর দেখিলে তিনি অস্থির হইয়া পড়িতেন। তিনি প্রায়ই রাসূলে করীম (স)-কে উদ্ধৃত করিয়া বলিতেনঃ কবর হইল পরকালীন জীবনের প্রথম পর্যায়। এই পর্যায়টি সহজে ও নিরাপদে অতিক্রম করা গেলে পরবর্তী সব কয়টি পর্যায়ই সহজে অতিক্রান্ত হইবে বলিয়া আশা করা যায়। পক্ষান্তরে ইহাতেই বিপদ দেখা দিলে পরবর্তী সব পর্যায়ই কঠিন হইয়া দাঁড়াইবে।
হযরত উসমান (রা) ইসলামের প্রায় সব কয়টি যুদ্ধে রাসূলে করীম (স)-এর সহগামী ছিলেন এবং সর্বক্ষেত্রেই তিনি তাঁহার জন্য আত্মোৎসর্গীকৃত হইয়াছিলেন। দৈনন্দিন জীবনেও রাসূলে করীম (স)-এর দুঃখ-কষ্ট দূরীভূত করার জন্য তিনি সর্বদা সচেতন ও সজাগ-সক্রিয় থাকিতেন। রাসূলে করীম (স)-এর প্রতি ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা,ভক্তি ও সম্মান প্রদর্শনে তিনি অতিশয় সচকিত থাকিতেন। তিনি যে হস্তে রাসূলে করীম (স)-এর হস্ত স্পর্শ করিয়া ইসলামের বায়’আত গ্রহণ করিয়াছিলেন, উহাতে জীবনে কোন দিন একবিন্দু মালিন্যও লাগিতে দেন নাই। তিনি আপন খিলাফত আমলে রাসূলে করীম (স)-এর পরিবারবর্গের প্রয়োজন পূরণের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন, যেন তাঁহাদিগকে কোনরূপ দৈন্য ও অসুবিধার সম্মুখীন হইতে না হয়।
রাসূলে করীম (স)-এর প্রতি তাঁহার এইরূপ অকৃত্রিম ও সুগভীর ভক্তি-শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠাপূর্ণ ভালোবাসা ও আন্তরিকতার অনিবার্য পরিণতি এই ছিল যে, তিনি ছোট-বড় প্রত্যেকটি ব্যাপারেই তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া চলিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা চালাইতেন। সাধারণ কথা, কাজ ও গতিবিধিতেও রাসূলে করীম (স)-এর হুবহু অনুসরণ করিবার জন্য তাঁহার চেষ্টার কোন ত্রুটি হইত না। নবী করীম (স)-কে তিনি যেভাবে অযু করিতে দেখিয়াছেন, নামায পড়িতে দেখিয়াছেন, লাশের প্রতি আচরণ করিতে দেখিয়াছেন, তিনিও এইসব কাজ ঠিক সেইভাবেই সম্পন্ন করিতেন। কাহাকেও রাসূলে করীম (রা)-এর সুন্নাতের বিপরীতে বা ভিন্নতর রীতিতে কোন কাজ করিতে দেখিলে সঙ্গে সঙ্গেই তিনি উহাতে আপত্তি জানাইতেন এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিতেনঃ ‘তুমি কি রাসূলে করীম (স)-কে এই কাজ করিতে নিজ চক্ষে দেখ নাই’। বস্তুত রাসূলে করীম (স)-এর এইরূপ আক্ষরিক অনুসরণই ছিল একজন আদর্শবাদী সাহাবী হিসাবে তাঁহার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।
লজ্জাশীলতা ও বিনয়-নম্রতা ছিল হযরত উসমান (রা)-এর এক বিশিষ্ট ধরণের গুণ। ঐতিহাসিক ও জীবনচরিত রচয়িতাগণ তাঁহার লজ্জাশীলতার কথা বিশেষ গুরুত্ব সহকারে উল্লেখ করিয়াছেন। স্বয়ং রাসূলে করীম (স)-ও তাঁহার এই লজ্জাশীলতাকে বিশেষ মর্যাদা দিতেন বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছে।
হযরত উসমান (রা) তাঁহার স্বভাবসুলভ লাজুকতা, বার্ধক্যজনিত দুর্বলতা এবং সীমাহীন পারিবারিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে লালিত-পালিত হওয়ার কারণে উত্তম পোশাক-পরিচ্ছদ ও উৎকৃষ্ট খাদ্য গ্রহণে অভ্যস্থ ছিলেন। হযরত উমর ফারুক (রা)-এর ন্যায় কষ্ট-সহিষ্ণুতা ও প্রকৃতিগত কঠোরতা তাঁহার ছিলনা। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি জাঁকজমক ও বিলাস-ব্যসনপুর্ণ জীবন যাপন করিতেন, এমন কথা মনে করিবার কোন কারণ নাই।সত্য কথা এই যে, তিনি নিজে বিপুল ধন-সম্পদের অধিকারী হইয়াও কিছুমাত্র বড়লোকী জীবন-মান গ্রহণ করেন নাই। এই কারণে বিলাসিতা ও জাঁকজমকপূর্ণ জীবনধারা ছিল তাঁহার নিকট অত্যন্ত অপছন্দনীয়।
তিনি স্বভাবগতভাবে অতি বিনয়ী ও নিরহংকার ছিলেন। তাঁহার পারিবারিক কাজকর্মের জন্য বহু সংখ্যক লোক নিয়োজিত থাকা সত্ত্বেও নিজের যাবতীয় কাজকর্ম তিনি নিজেই সম্পাদন করিতেন এবং ইহাতে কোনরূপ লজ্জা বা অপমান বোধ করিতেন না। ব্যক্তিগত জীবনে কার্পণ্য কাহাকে বলে তাহা তিনি জানিতেন না। তিনি ছিলেন তদানীন্তন আরবের সর্বাধিক ধনাঢ্য ব্যক্তি। সেই কারণে দানশীলতা ছিল তাঁহার চরিত্রের প্রধান ভূষণ। তিন নিজের ধন-সম্পদ নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানে নয়- সাধারণ জনকল্যাণেই ব্যয় করিতে থাকিতেন। ইসলামের কাজে তাঁহার ধন-সম্পদ যতটা ব্যয়িত হইয়াছে, তদানীন্তন সমাজে এই দিক দিয়া অন্য কেহই তাঁহার সমতুল্য হইতে পারে না।
মদীনায় পানির সমস্ত কূপ লবনাক্ত ছিল। শুধু ‘রুমা’ নামক একটি কুপ হইতে মিষ্টি পানি পাওয়া যাইত; কিন্তু উহার মালিক ছিল জনৈক ইয়াহুদী। হযরত উসমান (রা) জনগণের প্রয়োজন পূরণের উদ্দেশ্যে উক্ত কূপটি বিশ হাজার দিরহামের বিনিময়ে ক্রয় করিয়া জনসাধারণের জন্য ওয়াকফ করিয়া দেন। নগরীতে মুসলমানদের সংখ্যা দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পাওয়ার দরুণ মসজিদে নববী সম্প্রসারিত করা অপরিহার্য হইয়া পড়িলে তিনি বিপুল অর্থ ব্যয় করিয়া এই অত্যাবশ্যকীয় কাজটি সম্পন্ন করিয়া ফেলেন। অনুরূপভাবে তাবুক যুদ্ধকালে নিজস্ব তহবিল হইতে অর্থব্যয় করিয়া তিনি সহস্র মুজাহিদকে সশস্র ও সুসংগঠিত করিয়া দেন। অথচ এই সময় মুসলমানদের দৈন্য ও দারিদ্র তাঁহাদিগকে নির্মমভাবে পীড়িত ও উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিয়াছিল।এক কথায় বলা যায়, উসমান (রা) ছিলেন এক অতুলনীয় দানশীল ব্যক্তি। ব্যক্তি-মালিকানার ধন-সম্পদ হওয়া সত্ত্বেও তাঁহার হস্তে উহা সাধারণ জনগণের কল্যাণে ব্যাপকভাবে ব্যয়িত হইয়াছে। পুঁজিবাদী বিলাস-ব্যাসন কিংবা শোষণ-পীড়নের মালিন্য তাঁহার ব্যক্তি মালিকানাকে কিছুমাত্র কলুষিত করিতে পারে নাই।১ {বদান্যতার প্রবাদ পুরুষঃ বদান্যতা বা দানশীলতা ব্যাপারে হযরত উসমান (রা) ছিলেন অবিশ্বাস্য রকমের উদারহস্ত। তাঁহার দান খয়রাতের এক-একটি ঘটনা ছিল রূপকথার মত। একদা জনৈক অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি সাহায্যের প্রত্যাশায় হযরত উসমান (রা)-এর শরণাপন্ন হইল। লোকটি যখন হযরত উসমান (রা)-এর বাড়ীর সন্নিকটে পৌঁছিল, তখন তিনি (উসমান)নিবিষ্টচিত্তে মাটি হইতে সরিষার দানা খুঁটিয়া খুঁটিয়া তুলিতেছিলেন। এই দৃশ্য অবলোকন করিয়া আগন্তুক লোকটি ভীষণভাবে হতাশাগ্রস্ত হইয়া পড়িল। সে উসমান (রা)-কে এক নিকৃষ্ট কৃপণ ব্যক্তি ভাবিয়া ফিরিয়া যাইতে উদ্যত হইল। সহসা উসমান (রা) আগন্তুক লোকটিকে দেখিতে পাইলেন। তিনি তাহাকে কাছে ডাকিয়া এইভাবে ফেরত যাওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। লোকটি সব ঘটনা আদ্যপান্ত খুলিয়া বলিল। উসমান (রা)লোকটির কথা শুনিয়া একটু মুচকি হাসিলেন। ঘটনাক্রমে এই সময় পণ্য-সামগ্রী বোঝাই সাতটি উট আসিয়া সেখানে থামিল। উসমান (রা)উটসহ সমগ্র পণ্য-সামগ্রীই আগন্তুককে দান করিয়া দিলেন। এই ঘটনায় লোকটি একেবারে হতবাক হইয়া গেল এবং উসমান (রা) সম্পর্কে তাহার বিরুপ ধারণার জন্য বারবার অনুশোচনা প্রকাশ করিতে লাগিল।–সম্পাদক}
হযরত উসমান (রা) ছিলেন ধৈর্য ও সহনশীলতার বাস্তব প্রতীক। দুঃখ-কষ্ট ও বিপদ-মুছিবত যত বড় এবং যত মারাত্মকই হউক না কেন, সবর,ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার শানিত অস্ত্রে তিনি উহার সব কিছুই ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দিতেন এবং সমস্ত প্রতিকূলতার মুকাবিলায় তিনি পর্বতের ন্যায় অবিচলরূপে দাঁড়াইয়া থাকিতেন।
তাঁহার জীবনধারা ছিল অত্যন্ত সুশৃঙ্খল, পরিমিত ও সংযত। দিনের বেলায় খিলাফতের দায়িত্ব পালনে গভীরভাবে ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও রাত্রের বেশীর ভাগ সময় তিনি নামায ও আত্মিক সাধনায় নিমগ্ন থাকিতেন। অনেক সময় তিনি সমগ্র রাত্রিও জাগিয়া কাটাইতেন এবং এক রাকয়াতেই পূর্ণ কুরআন মজীদ পড়িয়া ফেলিতেন। এই ধরণের ঘটনা তাঁহার জীবনে বহুবার সংঘটিত হইয়াছে।যে কয়জন সাহাবী ইসলামের পূর্বে জাহিলিয়াতের জামানায় লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন, হযরত উসমান (রা) ছিলেন তাঁহাদের অন্যতম। এই কাজে তাঁহার যোগ্যতা ও দক্ষতা স্বয়ং নবী করীম (স) কর্তৃকও স্বীকৃত ও প্রশংসিত হইয়াছে। এই জন্য অন্যান্যের সঙ্গে তাঁহাকেও অহী লেখার কাজে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। হযরত রাসূলে করীম (স)-এর প্রতি যখনই অহী নাযিল হইত, তখনই উহা লিখিয়া রাখার সুষ্ঠু ও নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছিল। হযরত উসমান (রা)এই কাজে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন।
অবশ্য লেখার কাজে পারদর্শী হইলেও বক্তৃতা-ভাষণে তিনি অতটা সক্ষম ছিলেন না। খলীফা নির্বাচিত হওয়ার পর সর্বপ্রথম মিম্বারের উপর আরোহণ করিয়া তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে কোন ভাষণ না দিয়া শুধু বলিলেনঃ
আমার পূর্ববর্তী খলীফাদ্বয়-আবূ বকর ও উমর (রা) পূর্বেই প্রস্তুতি লইয়া আসিতেন। আমিও ভবিষ্যতে প্রস্তুত হইয়াই আসিব। কিন্তু আমি মনে করি, বক্তৃতা-ভাষণে সক্ষম ইমামের (নেতার) চেয়ে কর্মদক্ষ ইমামই তোমাদের জন্য প্রয়োজন।
এই কথাটুকু বলিয়া তিনি মিম্বারের উপর হইতে নীচে অবতরণ করিলেন। অবশ্য ইহার পর তিনি বিভিন্ন সময় প্রয়োজন মত বক্তৃতা-ভাষণ দিয়াছেন এবং উহাতে তাঁহার যোগ্যতারও যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইত। তাঁহার ভাষণসমূহ খুবই সংক্ষিপ্ত,জ্ঞানগর্ভ এবং উচ্চমানের হইত।
হযরত উসমান (রা)-এর বর্ণিত একটি হাদীসে বলা হইয়াচেঃ ‘কুরআন মজীদ পড়া ও পড়ানো অতি উত্তম সওয়াবের কাজ’। এই হাদীস অনুযায়ী তিনি নিজে জীবনের শেষ মুহূর্তে পর্যন্ত আমল করিয়াছেন। সম্ভবতঃ এই কারণেই তিনি অধিকাংশ সময় কুরআন মজীদ তিলাওয়াতে অতিবাহিত করিতেন। তিনি পূর্ণ কুরআনেরও হাফিয ছিলেন। কুরআনের সহিত তাঁহার অন্তরের গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। জীবনের শেষ মুহূর্তে সশস্ত্র বিদ্রোহীরা যখন তাঁহাকে চতুর্দিক হইতে পরিবেষ্টন করিয়া ফেলিয়াছিল, তখনও তিনি সর্বদিক হইতে নিজেকে গুটাইয়া আনিয়া গভীর তন্ময়তা সহকারে কুরআন তিলাওয়াতে নিমগ্ন হইয়াছিলেন।
তিনি অহী-লেখক ছিলেন বিধায় কুরআন সম্পর্কিত জ্ঞানে তাঁহার অতুলনীয় পারদর্শিতা ছিল। বিভিন্ন জটিল বিষয়ে কুরআন হইতে দলীল পেশ করা এবং কুরআন হইতে শরীয়াতের বিধান খুঁজিয়া বাহির করায় তিনি বিশেষ দক্ষতা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। কুরআন-বিরোধীদের ষড়যন্ত্র হইতে কুরআন মজীদকে সুরক্ষিত করার ব্যাপারেও তাঁহার অবদান চির অম্লান হইয়া থাকিবে। হাদীস বর্ণনার ব্যাপারে তিনি অন্যান্য সাহাবীদের চেয়ে অধিক সতর্কতা অবলম্বন করিতেন। এই কারণে তিনি মাত্র ১৪৬টি হাদীস রাসূলে করীম (স) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। অবশ্য এই সতর্কতা অনেকটা ব্যক্তিগত ব্যাপার। ব্যক্তিগত রুচি ও দৃষ্টিকোণ হইতেই ইহা উৎসারিত। এই কারণে একই নবীর সাহাবী হওয়া সত্ত্বেও বর্ণিত হাদীসের সংখ্যার দিক দিয়া সাহাবীদের মধ্যে বিরাট তারতম্য হইয়াছে এবং ইহা ছিল খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার।
হযরত উসমান (রা) হযরত আবূ বকর (রা) হযরত উমর ফারুক (রা) এবং হযরত আলী (রা)-র ন্যায় বড় বড় মুজতাহিদদের মধ্যে গণ্য না হইলেও শরীয়াতের বহু ব্যাপারে তিনি ইজতিহাদ করিয়াছেন। এই ধরণের ইজতিহাদ এবং বিভিন্ন মিমাংসা ও ফয়সালা ইসলামের গ্রন্থাবলীতে উল্লেখিত হইয়াছে। বিভিন্ন বিষয়ে তাঁহার জ্ঞান ছিল অতুলনীয়। তিনি নিজে প্রত্যেক বৎসরই হজ্জ উদযাপন করিতেন ও ‘আমীরে হজ্জ’-এর দায়িত্ব পালন করিতেন। খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পরও তিনি একটিবারও হজ্জ উদযাপন হইতে বিরত থাকেন নাই। শরীয়াতের ব্যাপারে তিনি বিভিন্ন সময় যেসব রায় দিয়াছেন ও বিচার-ফয়সালা করিয়াছেন, তাহা ইসলামী শরীয়াতের বাস্তব ব্যাখ্যার দৃষ্টিতে চিরকাল অতীব মূল্যবান সম্পদ হইয়া থাকিবে। বিভিন্ন ইজতিহাদী ব্যাপারে অন্যান্য সাহাবীদের সহিত তাঁহার মতবৈষম্য ঘটিয়াছে। কিন্তু তিনি কুরআন-হাদীস যুক্তির ভিত্তিতে যে রায় দিতেন, তাহাতে তিনি সুদৃঢ় আত্মবিশ্বাসের দরুণই অবিচল হইয়া থাকিতেন। হযরত উসমান (রা) একজন সফল ও সার্থক ব্যবসায়ী ছিলেন বলিয়া হিসাব জ্ঞানে তাঁহার বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। এই কারণে ‘ইলমুল-ফারায়েজ’ বা উত্তরাধিকার বণ্টন-বিদ্যায় তাঁহার বুৎপত্তি ছিল সর্বজনস্বীকৃত। এই বিদ্যার মৌলিক নীতি প্রণয়নে হযরত জায়েদ ইবনে সাবিত (রা)-এর সঙ্গে তাঁহার অবদান অবশ্য স্বীকৃতব্য। সাহাবীগণ মনে করিতেন, ফারায়েজ বিদ্যায় এই দুইজন পারদর্শীর অন্তর্ধানের পূর্বে ইহার সঠিক প্রণয়ন না হইলে এই বিদ্যাই বিলুপ্ত হইয়া যাইবে।
হযরত উসমান (রা)-এর খিলাফত
হযরত উসমান (রা)-এর বয়স যখন চৌত্রিস বৎসর, তখন মক্কা নগরে দ্বীন-ইসলামের দাওয়াত সূচিত হয়। তদানীন্তন সামাজিক নিয়ম-প্রথা,আচার-আচরণ এবং আরবের ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির বিচারে হযরত উসমান (রা)-এর নিকট তওহীদের দাওয়াত প্রথম পর্যায়ে নিতান্তই অপরিচিত থাকিয়া গিয়াছিল। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তিনি তাঁহার ব্যক্তিগত পবিত্রতা,সত্যানুসন্ধিৎসা ও ন্যায়পরায়ণতার কারণে দ্বীন-ইসলামের দাওয়াত কবুল করার প্রস্তুত হইয়াছিলেন।
ইসলাম গ্রহন
নবুয়্যাতী মিশনের প্রথম পর্যায়েই হযরত আবূ বকর (রা) ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন।ইহার পরই তিনি ইসলাম প্রচারের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। প্রথমে তিনি তাঁহার বন্ধু-বান্ধব ও পরিচিতজনদের মধ্যে ইসলামী দাওয়াতের প্রচার শুরু করেন। হযরত উসমান (রা)-এর সাথে তাঁহার গভীর সম্পর্ক এবং পরিচিত ছিল। একদিন তিনি তাঁহার নিকট ইসলামী দাওয়াতের ব্যাখ্যা পেশ করেন। হযরত উসমান (রা)সবকিছুই শুনিয়া এই মহাসত্যের প্রতি প্রচণ্ড আকর্ষণ অনুভব করিলেন এবং নবী করীম (স)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া ইসলাম কবুল করার জন্য প্রস্তুত হইলেন। পথিমধ্যে নবী করীম (স) সহিত সাক্ষাৎ হইলে তিনিও উসমানকে ইসলাম কবুল করার জন্য মর্মস্পর্শী ভাষায় আহ্বান জানাইলেন। এই ঘটনার প্রসঙ্গে হযরত উসমান (রা) বলিলেনঃ “রাসূলে করীমের (স)-এর মুখ-নিঃসৃত কথা কয়টি শুনিবার সঙ্গে সঙ্গে আমার হৃদয়ে প্রবল আলোড়নের সৃষ্টি হইল। তখন স্বতঃস্ফূর্তভাবে আমি শাহাদাতের কালেমা পাঠ করিতে শুরু করিয়া দিলাম এবং রাসূলে করীম (স)-এর হাতে হাত দিয়া ইসলাম গ্রহণ করিলাম’।
হযরত উসমান (রা) মক্কার অন্যতম শক্তিশালী উমাইয়া বংশের লোক ছিলেন। আর গোটা বংশটিই ছিল রাসূলে করীম (স)-এর বংশ বনু হাশিমের চরম প্রতিদ্বন্দ্বী ও বিরুদ্ধবাদী। উমাইয়া বংশের লোকেরা রাসূলে করীম (স)-এর উত্তরোত্তর সাফল্য ও বিজয় লাভে বিশেষভাবে ভীত ছিল। কেননা উহার ফলে সমগ্র নেতৃত্ব ও প্রাধান্য উমাইয়া বংশের হস্তচ্যুত হইয়া বনু হাশিম বংশের হস্তগত হওয়ার প্রবল আশংকা ছিল। তদানীন্তন গোত্রবাদি সমাজে এই ব্যাপারটি যে কতটা সাংঘাতিক ছিল, গোত্রবাদের ধর্ম ও চরিত্র সম্পর্কে অবহিত লোকেরাই তাহা সহজেই অনুধাবন করিতে পারেন। কিন্তু হযরত উসমান (রা)-এর হৃদয়-দর্পণ বংশীয় ও গোত্রীয় হিংসাদ্বেষের কলুষ-কালিমা হইতে মুক্ত ও স্বচ্ছ ছিল বলিয়া শত বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও ইসলাম গ্রহণ করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া দাড়ায় নাই। তিনি যখন ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন তখন মুসলমানদের মোট সংখ্যা ছিল মাত্র পঁয়ত্রিশ কিংবা ছত্রিশ।
তাঁহার ইসলাম গ্রহণের পর নবী করীম (স) নিজেই আগ্রহী হইয়া তাঁহার কন্যা হযরত রুকাইয়া (রা)-র সহিত হযরত উসমান (রা)-এর বিবাহ সম্পন্ন করেন।
হিজরাত
মক্কা নগরে ইসলামের ক্রমবর্ধমান প্রসার ও শক্তি বৃদ্ধি ঘটিতে দেখিয়া মুশরিক সমাজ খুবই চিন্তান্বিত ও বিচলিত হইয়া পড়িল। তাহাদের ক্রোধ ও অসন্তোষ ক্রমশঃতীব্র হইতেও তীব্রতর হইয়া উঠিতে লাগিল। ইহার ফলে হযরত উসমান (রা)স্বীয় ব্যক্তিগত গুণগরিমা ও বংশগত মানমর্যাদা সত্ত্বেও ইসলামের জন্য অমানুষিক নির্যাতন ভোগ করিতে বাধ্য হন। ইসলাম ত্যাগে বাধ্য করার জন্য তাঁহার চাচা নিজে তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিত ও নির্মমভাবে প্রহার করিত। আত্মীয়স্বজনের মধ্য হইতে তেমন কেহই তাঁহাকে এই অবস্থা হইতে উদ্ধার করার জন্য আগাইয়া আসিতে প্রস্তুত হয় নাই। তাঁহার উপর এই অত্যাচারের মাত্রা ক্রমশঃবৃদ্ধি পাইতে থাকে। শেষ পর্যন্ত ইহা হযরত উসমান (রা)-এর পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠে। অবশেষে তিনি নবী করীম (স)-এর ইংগিতে একটি কাফেলা লইয়া সপরিবারে আবিসিনিয়ায় (ইথিওপিয়া) হিজরাত করিয়া গেলেন। কেবলমাত্র সত্য দ্বীন ও সত্য আদর্শের জন্য এই কাফেলাটি স্বদেশবাসীদের ত্যাগ করিয়া এক অজানা পথে রওনা হইয়া গেল।
আবিসিনিয়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইয়া যাওয়ার পর দীর্ঘদিন পর্যন্ত নবী করীম (স) তাঁহাদের সম্পর্কে কোন সংবাদ জানিতে পারেন নাই। এই কারণে তিনি খুবই চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন। কিছুদিন পর তিনি যখন তাঁহাদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছার সংবাদ জানিতে পারিলেন, তখন স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলিয়া উঠিলেনঃ
*******(আরবী)
‘এই জাতির মধ্য হইতে উসমানই সপরিবারে সর্বপ্রথম হিজরাতকারী ব্যক্তি’।
হযরত উসমান (রা) আবিসিনিয়ায় কয়েক বৎসর পর্যন্ত অবস্থান করেন। সেখান হইতে প্রত্যাবর্তনের পর কিছুদিন যাইতে না যাইতেই মদীনায় হিজরাত করার আয়োজন সুসম্পন্ন হয়। তখন উসমান (রা)-ও সপরিবারে মদীনায় চলিয়া গেলেন। হযরত উসমান (রা) ইসলাম ও কুফরের প্রথম সম্মুখ-সংঘর্ষে অর্থাৎ বদর যুদ্ধে যোগদান হইতে ঘটনাবশতঃই বিরত থাকিতে বাধ্য হন। এই যুদ্ধের সময় তাঁহার স্ত্রী নবী-তনয়া রুকাইয়া (রা) কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়েন। এই কারণে নবী করীম (স)তাঁহাকে যুদ্ধে যাওয়ার অনুমতি না দিয়া রোগিনীর সেবা-শুশ্রূষা করার দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দিলেন। কিন্তু এই দুঃখে তিনি ভারাক্রান্ত হইয়া সারাটি জীবন অতিবাহিত করেন। ইসলামের প্রথম সমরে শরীক হইতে না পারার বেদনা তিনি জীবনে মুহূর্তের তরেও ভুলিতে পারেন নাই।
কিন্তু ইহার পর যে কয়টি যুদ্ধই সংঘটিত হইয়াছে, উহার প্রত্যেকটিতেই তিনি পূর্ণ সাহসিকতা ও বীর্যবত্তা সহকারে রাসূলে করীম (স)-এর সঙ্গী হইয়াছেন। ষষ্ঠ হিজরী সনে নবী করীম (স) কা’বা জিয়ারতের উদ্দেশ্যে সদলবলে মক্কার পথে রওয়ানা হইয়া যান। পথিমধ্যে হুদাইবিয়া নামক স্থানে কাফেলাটি প্রতিরুদ্ধ হইলে নবী করীম (স)উসমান (রা)-কে রাষ্ট্রদূত হিসাবে কাফির মুশরিকদের সঙ্গে কথাবার্তা বলার দায়িত্ব দিয়া মক্কায় প্রেরণ করেন। মক্কায় তাঁহাকে কাফির মুশরিকরা অবরুদ্ধ করিয়া ফেলে। কয়েকদিন পর্যন্ত তাঁহার সম্পর্কে কোন সংবাদ জানিতে না পারায় নবী করীম (স) এবং মুসলমানগণ বিশেষভাবে উদ্বিগ্ন হইয়া পড়েন। এই সময় চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়ে যে, হযরত উসমান (রা)-কে শহীদ করা হইয়াছে। এই খবর শুনা মাত্রই নবী করীম (স) ইহার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য সঙ্গের চৌদ্দশত সাহাবীর নিকট হইতে বায়’আত গ্রহণ করেন।ইসলামের ইতিহাসে ইহা ‘বায়’আতে রিজওয়ান’- আল্লাহ্র সন্তোষলাভে চরম আত্মোৎসর্গের প্রতিশ্রুতি- নামে অভিহিত ও স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হইয়া রহিয়াছে।
খলীফারূপে নির্বাচন
হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর পর হযরত উমর ফারুক (রা) দীর্ঘ দশটি বৎসর পর্যন্ত ইসলামী খিলাফতের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি অজ্ঞাতনামা আততায়ীর ছুরিকাঘাতে আহত হইয়া পড়িলে জীবনের সায়াহ্নকালে পরবর্তী খলীফা নির্বাচনের জন্য ছয় সদস্য-বিশিষ্ট একটি বোর্ড গঠন করিয়া দেন। হযরত আলী, হযরত উসমান, হযরত জুবাইর, হযরত তালহা, হযরত সায়াদ, হযরত সায়াদ ইবনে আক্কাস এবং হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) এই বোর্ডের সম্মানিত সদস্য ছিলেন। তিন দিনের মধ্যেই খলীফা নির্বাচনের কাজ সম্পন্ন করার জন্যও এই বোর্ডকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। হযরত উমর ফারুক (রা)-এর কাফন-দাফন সম্পন্ন হওয়ার পর খলীফা নির্বাচনের ব্যাপারে মনোযোগ দেওয়া হয়। দুইদিন পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলাপ-আলোচনা, মত বিনিময়, জনমত যাচাই ইত্যাদি কাজে অতিবাহিত হইয়া যায়। তৃতীয় দিনে হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা)-এর প্রস্তাবক্রমের হযরত উসমান (রা)-কে খলীফা নির্বাচন করা হয়। সমবেত সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে হযরত আলী (রা) সর্বপ্রথম তাঁহার হাতে ‘বায়’আত’ করেন। অতঃপর উপস্থিত জনতা বায়’আতের জন্য ভাঙিয়া পড়ে। এইভাবে ২৪ হিজরী সনের মুহাররম মাসের ৪ তারিখ সর্বসম্মতিক্রমে হযরত উসমান (রা) খলীফা পদে বরিত হন এবং খিলাফতে রাশেদার শাসনভার গ্রহণ করে।
খিলাফতের দায়িত্ব পালন
হযরত উমর ফারুক (রা) তাঁহার খিলাফত আমলে সিরিয়া, মিশর ও পারস্য জয় করিয়া সুসংবদ্ধ ইসলামী রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন। উপরন্তু শাসন-শৃঙ্খলা ও প্রশাসন ব্যাবস্থায় তিনি একটা শাসনতান্ত্রিক কার্যবিধি প্রবর্তন করিয়া গিয়াছিলেন। এই কারণে হযরত উসমান (রা)-এর পক্ষে খিলাফতের দায়িত্ব পালন অনেকটা সহজ হইয়াছিল। এই কাজে তিনি যুগপৎ হযরত সিদ্দীকের নমনীয়তা, কোমলতা ও দয়ার্দ্রতা এবং হযরত উমর ফারুক (রা)-এর প্রশাসনিক দক্ষতা, বিচক্ষণতা ও কঠোরতা অনুসরণ করিয়া চলিতেন। এক বৎসরকাল পর্যন্ত তিনি পূর্ববর্তী প্রশাসন ব্যাবস্থা অপরিবর্তিত রাখিয়াছিলেন। প্রাক্তন খলীফার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তিনি হযরত সায়াদ ইবনে আক্কাস (রা)-কে কুফার গভর্নর নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ইহা ছিল খলীফা হযরত উসমান (রা) কর্তৃক সম্পাদিত প্রথম নিয়োগ। পরে অবশ্য ২৬ হিজরী সনে তিনি তাঁহাকে পদচ্যুতও করিয়াছিলেন।
উসমানীয় খিলাফতের প্রথম বৎসরের মধ্যেই ত্রিপলি, আলজিরিয়া ও মরক্কো অধিকৃত হয়। ইহার ফলে স্পেনের দিকে মুসলমানদের অগ্রগতির দ্বার উন্মুক্ত হয়। সাইপ্রাসের উপর হযরত উমর ফারুক (রা)-এর খিলাফত আমলেই কয়েকবার সৈন্য অভিযান পরিচালনা করা হইয়াছিল। ২৮ হিজরী সনে হযরত আমীর মুয়াবিয়ার নেতৃত্বে ভূ-মধ্য সাগরে অবস্থিত এই গুরুত্বপূর্ণ দ্বীপটির উপর মুসলিম বিজয়ের পতাকা উড্ডীন হয়। এইভাবে হযরত উসমান (আ)-এর খিলাফত আমলে ইসলামী রাজ্য সীমার বিপুলে বিস্তৃত ও সম্প্রসারন সাধিত হয়। কাবুল, হিরা, সিজিস্তান ও নিশাপুরে এই সময়ই ইসলামী খিলাফতের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।
হযরত উসমান (রা)-এর দ্বাদশ বর্ষীয় খিলাফত আমলের প্রথম ছয়টি বৎসর পূর্ণ শান্তি, শৃঙ্খলা ও নিয়মতান্ত্রিকতার মধ্যে অতিবাহিত হয়। বহু দেশ নিয়া গঠিত বিশাল এলাকা ইসলামী খিলাফতের অন্তর্ভুক্ত হয়। বায়তুলমালে আয়ের পরিমাণ বিপুলভাবে বৃদ্ধি পায়। কৃষি, ব্যবসায় ও প্রশাসন ক্ষেত্রের অসাধারণ উন্নতি জন-জীবনে অভূতপূর্ব সমৃদ্ধি আনিয়া দেয়। হযরত উসমান (রা)-এর খিলাফতের উল্লেখযোগ্য অবদান হইল ইসলামের বিশাল সাম্রাজ্যের প্রশাসন ব্যবস্থা উতরোত্তর দৃঢ়তর করিয়া তোলা এবং তীক্ষ্ণবুদ্ধিমত্তা, নির্ভুল ব্যবস্থাপনা ও উত্তম কর্মনীতির সাহায্যে বিজিত জাতিসমূহের বিদ্রোহাত্মক ভূমিকা ও তৎপরতা দমন করিয়া শান্তিপূর্ণ জীবন প্রতিষ্ঠা করা।
খলীফা হিসাবে হযরত উসমান (রা)-কে বহু সংখ্যক বিদ্রোহ দমন করিতে হইয়াছে। তাঁহার আমলে মিশরে বিদ্রোহের ঝাণ্ডা উত্তোলিত হয়, আর্মেনিয়া ও আযারবাইজান অঞ্চলের অধিবাসীরা ‘খারাজ’ দেওয়া বন্ধ করিয়া দেয়, খোরাসানবাসিরাও বিদ্রোহের মস্তক উত্তোলন করে। এইসব বিদ্রোহ ছিল বিজিত জাতিসমূহের মনে ধুমায়িত বিদ্বেষ ও প্রতিহিংসামূলক বিষ-বাষ্পের বিস্ফোরণেরই পরিণতি। কিন্তু হযরত উসমান (রা) বিশেষ সতর্কতা ও বিচক্ষণতা সাহায্যে উহা দমন করিতে সক্ষম। কঠোরতা-কোমলতা সমন্বিত কর্মনীতি ফলে এই সমস্ত এলাকার জনগণ ইসলামী খিলাফতের আনুগত্য স্বীকার করিয়া লয়।
সামুদ্রিক বিজয়াভিযান হযরত উসমান (রা)-এর খিলাফত আমলের একটি বিশেষ অবদান। হযরত উমর (রা)-র সতর্কতামূলক নীতির ফলে সে আমলে মুসলমানদিগকে বিপদসংকুল সামুদ্রিক পথে অভিযানে প্রেরণ শুরু হইতে পারে নাই। কিন্তু হযরত উসমান (রা)-এর দুঃসাহসিকতা বিপদ-শংকাকে সহজেই অতিক্রম করা সম্ভবপর করিয়া দিয়াছিল। তাঁহার নিখুঁত সমর পরিকল্পনার ফলে রোমান সম্রাটের পাঁচশতটি যুদ্ধ জাহাজ সমন্বিত বিশাল নৌ বাহিনীকে চরম পরাজয় বরণ করিতে বাধ্য করা হয়।
খিলাফতে শাসন পদ্ধতি
খিলাফতে রাশেদার শাসন-পদ্ধতি পরামর্শ ভিত্তিক রাষ্ট্রব্যবস্থা হিসাবে আরম্ভ হইয়াছিল। হযরত উমর ফারুক (রা)এই ব্যবস্থাকে অধিকতর সুদৃঢ় ও সুসংবদ্ধও করিয়া তোলেন। হযরত উসমান (রা)-ও তাঁহার প্রাথমিক আমলে এই ব্যবস্থাকে অব্যাহত রাখেন। তবে শেষ পর্যায়ে বনু উমাইয়্যাদের অভ্যুত্থানের ফলে ইহাতে অনেক বিপর্যয় সূচিত হয়। হযরত উসমান উহা রোধ করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা চালাইতে থাকেন এবং এই উদ্দেশ্যে দায়িত্বশীল লোকদের দেওয়া যে কোন কল্যাণমূলক পরামর্শ তিনি নির্দ্ধিধায় গ্রহন করেন।
প্রসঙ্গতঃউল্লেখ্য যে, খিলাফতী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের মৌলিক অধিকার রক্ষা শাসকদের কর্মনীতি ও কার্যাবলীর প্রকাশ্য সমালোচনা করার নিরংকুশ অধিকার লাভ করিয়া থাকে। এই অধিকার এতটুকু হরণ করার ইখতিয়ার স্বয়ং খলিফাকেও দেওয়া হয় নাই। ইহা অনস্বীকার্য যে, হযরত উসমান (রা)-এর শেষ পর্যায়ে পরামর্শ ভিত্তিক ব্যবস্থায় কিছুটা ফাটল ধরিতে শুরু করিয়াছিল। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও গণ-অধিকার কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হইতে দেওয়া হয় নাই।
আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত দায়িত্বশীল ব্যক্তিরাই সাধারণতঃ দায়িত্বহীন ব্যক্তিদের তুলনায় অধিকতর উত্তম ও নির্ভুল মতামত প্রকাশে সক্ষ হইয়া থাকেন। এই কারণে বর্তমান কালেও বিভিন্ন সভ্য ও উন্নত দেশে এই ধরণের পরামর্শমূলক সংস্থা গঠন করা হইয়া থাকে। হযরত উসমান (রা) চৌদ্দশত বৎসর পূর্বে এই প্রয়োজন অনুভব করিয়া দায়িত্বশীল সরকারী কর্মচারীদের সমন্বয়ে এই ধরণের একটি পরামর্শ মজলিস গঠন করিয়াছিলেন। এই সংস্থার সদস্যদের নিকট হইতে সাধারণতঃলিখিত প্রস্তাবাবলী চাওয়া হইত। কুফা অঞ্চলে সর্বপ্রথম যখন শাসন-শৃঙ্খলায় উচ্ছৃংখলতা ও বিপর্যয় দেখা দেয়, তখন উহা নির্মূল করার উদ্দেশ্যে মজলিশ সদস্যদের নিকট হইতে লিখিত প্রস্তাবাবলী চাওয়া হইয়াছিল। মূল রাজধানীতেও মাঝে মাঝে এই ধরণের মজলিসের অধিবেশন আহ্বান করা হইত। ২৪ হিজরী সনে সমগ্র দেশের সার্বিক অবস্থার সংস্কার ও উন্নয়ন সাধন উদ্দেশ্যে রাজধানীতে এই মজলিসের যে অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, উহাতে এই পর্যায়ের অভিমতদানে সক্ষম অধিকাংশ দায়িত্বশীল কর্মচারীরা যোগদান করিয়াছিলেন।
প্রশাসন ব্যবস্থাকে অধিকতর সক্রিয় ও সুদৃঢ় করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে সমগ্র দেশের প্রদেশ ও জিলাভিত্তিক বিভাজন ও পুনর্গঠন ছিল অত্যন্ত জরুরী কাজ। হযরত উমর ফারুক (রা) সমগ্র সিরিয়া অঞ্চলের দামেশক, জর্ডান ও ফিলিস্তিন এই এই তিনটি ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে বিভক্ত করিয়াছিলেন। হযরত উসমান (রা) এই সমস্ত অঞ্চল একজন গভর্নরের অধীন করিয়া একটি বিশাল বিস্তীর্ণ প্রদেশ বানাইয়াছিলেন। প্রদেশের এই পুনর্গঠন শাসন-শৃঙ্খলার দৃষ্টিতে খুবই ফলপ্রসূ হইয়াছিল। শেষকালে সমগ্র দেশ যখন বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতার লীলাভূমিতে পরিণত হইয়াছিল, তখন সিরিয়ার সহিত সংশ্লিষ্ট জিলাসমূহ এই বিপর্যয় হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল।
হযরত উসমান (রা) সেনাধ্যক্ষের একটা নূতন পদ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ইহার পূর্ব পর্যন্ত প্রাদেশিক গভর্নরই সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে অবস্থিত সেনাবাহিনীর অধিনায়কের দায়িত্ব ও পালন করিতেন। ইহাতে কাজের বিশেষ অসুবিধা হওয়া অবধারিত ছিল।
খিলাফতে রাশেদার শাসন পদ্ধতিতে খলীফাই রাষ্ট্রপ্রধান। তিনি প্রশাসন বিভাগের সর্ব্বোচ্চ ক্ষমতায় আসীন। অধিনস্থ সমস্ত শাসনকর্তা ও প্রশাসন কর্মকর্তাদের উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখা খলিফারই অন্যতম প্রধান গুরুত্বপূর্ণ কাজ। হযরত উসমান (রা) স্বভাবতঃই দয়ার্দ্র-হৃদয় ও নরম মেজাজের লোক ছিলেন। ব্যক্তিগত পর্যায়ে ধৈর্য,সহিষ্ণুতা,ক্ষমা ও তিতিক্ষার বাস্তব প্রতিমূর্তি ছিলেন তিনি। কিন্তু দেশ শাসন ও রাষ্ট্রীয় কার্যাদি সুসম্পন্ন করার ব্যাপারে তিনি ছিলেন অত্যন্ত কঠোর ও ক্ষমাহীন। কর্মচারীদের জিজ্ঞাসাবাদ, খোঁজ খবর লওয়া এবং দোষত্রুটি পরিলক্ষিত হইলে কঠোর হস্তে উহার সংশোধন করা তাঁহার স্থায়ী কর্মনীতি ছিল। এইক্ষেত্রে কোন সম্মানিত কর্মচারীরাও যদি তেমন কোন দোষ ধরা পড়িত, তাহা হইলে তাহাকে পদচ্যুত করিতেও তিনি একবিন্দু কণ্ঠিত হইতেন না। বায়তুলমালের সম্পদ অপচয় ও আত্মসাৎকরণ এবং শাসনকর্তাদের বিলাসপূর্ণ জীবন যাপন তাঁহার দৃষ্টিতে ছিল ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ।
হযরত উসমান (রা) দেশের প্রশাসনযন্ত্র নিয়ন্ত্রন ও দোষত্রুটি সংশোধনের উদ্দেশ্যে একটি কেন্দ্রীয় ‘অনুসন্ধান কমিটি’ গঠন করিয়াছিলেন এবং রাজধানীর বাহিরে সর্বত্র উহাকে পাঠাইয়া দিতেন। কমিটি সমগ্র অঞ্চল ঘুরিয়া ঘুরিয়া প্রশাসন কর্মকর্তাদের কাজকর্ম ও জনগণের অবস্থা সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করিত। এতদ্ব্যতীত দেশের সাধারণ অবস্থা সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অবহিতি লাভের উদ্দেশ্যে হযরত উসমান (রা) জুম’আর দিন মিম্বারে দাঁড়াইয়া খুতবা শুরু করার পূর্বেই উপস্থিত জনতার নিকট দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের পরিস্থিতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করিতেন। উপস্থিত লোকদের কথা তিনি বিশেষ মনোযোগ সহকারে শুনিতেন। উপরন্তু সমগ্র দেশবাসীর নিকট সাধারণভাবে ঘোষণা করিয়া দেওয়া হইয়াছিল যে, কোন প্রশাসকের বিরুদ্ধে কাহারো কোনোরূপ অভিযোগ থাকিলে হজ্জের সময় তাহা যেন খলীফার সম্মুখে পেশ করা হয়। কেননা এই সময় ইসলামী খিলাফতের সমস্ত দায়িত্বশীল কর্মকর্তাকে মক্কা শরীফে বাধ্যতামূলকভাবে উপস্থিত থাকিতে হইত। এইভাবে লোকদের নিকট হইতে সামনা-সামনি অভিযোগ শ্রবণ ও উহার প্রতিকার সাধনের একটি সুষ্ঠু ব্যবস্থা হযরত উসমান (রা)-এর আমলে কার্যকর ছিল।
উল্লেখ্য, সাধারণ প্রশাসন ও শাসন-শৃঙ্খলা ব্যবস্থায় এবং বিভিন্ন শাসন বিভাগের হযরত উমর ফারুক (রা) প্রবর্তিত সংস্থাসমূহে হযরত উসমান (রা) কোনরূপ পরিবর্তন আনেন নাই। তিনি বরং উহাকেই অধিকতর সুসংবদ্ধ ও শক্তিশালী করিয়া তোলেন। ইহার পরিণতিতে রাজস্ব আদায়ে বিশেষ উন্নতি সাধিত হয়। ইহা ছাড়া নূতন অধিকৃত এলাকা হইতে রাজস্ব আদায়ের মাত্রা অনেক গুন বৃদ্ধি পায়। ফলে বায়তুলমালে ব্যয়ের খাত পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশী সমৃদ্ধ হইয়া উঠে এবং বৃত্তি ও ভাতা হিসাবে বিপুল অর্থ জনসাধারণের মধ্যে বণ্টন করা হয়। হযরত উসমান (রা)-এর আমলে খিলাফতের পরিধি যতই সম্প্রসারিত হইয়াছে, উন্নয়ন ও পুননির্মাণের কাজ ততই ব্যাপকতা লাভ করিয়াছে। এই সময় প্রাদেশিক সরকারগুলিকে বিভিন্ন অফিসের জন্য বহুসংখ্যক ইমারত নির্মাণ করা হয়। ইহার পাশাপাশি সড়ক, পুল ও মসজিদ নির্মাণের কাজও ব্যাপকভাবে চলিতে থাকে। দূরগামী যাত্রীদের জন্য বহুসংখ্যক সাধারণ মুসাফিরখানা স্থাপন করা হয়।
রাজধানীতে যাতায়াতের সব কয়টি পথ অধিকতর সহজগম্য ও আরামদায়ক করিয়া তোলা প্রশাসন ব্যবস্থার সুষ্ঠুতা বিধান ও জনগণের চলাচল নির্বিঘ্ন করার জন্য একান্তই অপরিহার্য ছিল। হযরত উসমান (রা) ইহার জন্য যথাবিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। ইহা ছাড়া তাঁহার উদ্যোগে মদীনা ও নজদের পথে পুলিশ-চৌকি স্থাপন করা হয় এবং মিষ্টি পানির জন্য কূপ খনন করা হয়। খায়বরের দিক হইতে কখনো কখনো বন্যার পানি আসিয়া মদীনাকে প্লাবিত ও নিমজ্জিত করিয়া দিত। ইহার ফলে শহরবাসীরা বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইত। এমনকি মসজিদে নববীরও উহার দরুণ ধসিয়া পড়ার আশংকা দেখা দিয়াছিল। এই কারণে হযরত উসমান (রা) মদীনার অদূরে একটি বিরাট বাঁধ নির্মাণ করাইয়াছিলেন। সাধারণ জনকল্যাণের দৃষ্টিতে হযরত উসমান (রা) নির্মিত এই ‘মাহজুর’ বাঁধ তাঁহার একটি উল্লেখযোগ্য অবদান।
মসজিদে নববীর সম্প্রসারণ ও পুননির্মাণে হযরত উসমান (রা)-এর হস্তে খুবই প্রশস্ত এবং সুদক্ষ ছিল। নবী করীম (স)-এর সময় এই উদ্দেশ্যে সংলগ্ন ভূমি খরীদ করিয়া তিনি মসজিদের জন্য ওয়াকফ করিয়া দিয়াছিলেন, এতদ্ব্যতীত তাঁহার নিজের খিলাফত আমলেও এই কাজটি পুনর্বার সম্পাদিত হইয়াছে। এই সময় মসজিদ সম্প্রসারণের বিশেষ প্রয়োজন দেখা দিয়াছিল;কিন্তু মসজিদ সন্নিহিত ঘর-বাড়ির মালিক ও অধিবাসীরা মসজিদের নৈকট্য হইতে বঞ্চিত হওয়ার আশংকায় ইহাতে কোনক্রমেই প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া শুনাইয়া সম্মত করিবার জন্য হযরত উসমান (রা) অব্যাহতভাবে প্রচেষ্টা চালাইতে থাকেন। এইভাবে সুদীর্ঘ পাঁচটি বৎসর অতিবাহিত হইয়া যায়। কোনোরূপ বল প্রয়োগ বা প্রশাসন যন্ত্রের সাহায্যে জমি অধিগ্রহনের কাজ করিতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। ২৯ হিজরী সনে সাহাবীগণের সহিত এই বিষয়ে বিশেষভাবে পরামর্শ করা হয়। ইহার পরিপ্রেক্ষিত হযরত উসমান (রা) জুম’আর দিন অত্যন্ত সংবেদনশীল কণ্ঠে জনতার সম্মুখে ভাষণ পেশ করেন। ভাষণে তিনি নামাজীদের সংখ্যা বৃদ্ধি ও মসজিদের সংকীর্ণতা জনিত সমস্যা বিশেষভাবে বুঝাইয়া বলেন। ভাষণ শ্রবণের পর লোকেরা সানন্দ চিত্তে ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজেদের ঘরবাড়ী ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত হন।
হযরত উমর ফারুক (রা) সামরিক বিভাগের জন্য যে ব্যবস্থাপনা করিয়া গিয়াছিলেন, হযরত উসমান (রা) উহাকে আরও উন্নত ও সম্প্রসারিত করেন। সামরিক বিভাগকে তিনিই সর্বপ্রথম প্রশাসন বিভাগ হইতে বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র করিয়া গড়িয়া তোলেন। তাঁহার উদ্যোগে প্রতিটি কেন্দ্রীয় স্থানে সেনা সংস্থাকে একজন বিশেষ সামরিক কর্মকর্তার অধীনে ন্যস্ত করিয়া দেওয়া হয়। ফলে দূরবর্তী যে কোন স্থানে সামরিক বাহিনী প্রেরণের প্রয়োজন অত্যন্ত তড়িৎবেগে পূরণ করার সুষ্ঠু ব্যবস্থা গৃহীত হয়। এই সময় ত্রিপলি, সাইপ্রাস, তিবরিস্তান ও আর্মেনিয়া অঞ্চলেও সামরিক ঘাঁটি সংস্থাপন করা হয়।
হযরত উসমান (রা)-এর খিলাফত আমলে ঘোড়া এবং উহার উষ্ট্র পালন এবং উহার সংরক্ষণের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপিত হয়। এই উদ্দেশ্যে সমগ্র শাসনাধীন অঞ্চলে বিশাল চারণ ভূমি গড়িয়া তোলা হয়। রাজধানীর আশেপাশেও অসংখ্য চারণ ভূমি তৈয়ার করা হয় এবং চারণ ভূমির নিকটেই পানির ব্যবস্থা করা হয়।
দ্বীন-প্রচারের কাজ
খলীফা মূলত নবী করীম (স)-এর উত্তরাধিকারী, স্থলাভিষিক্ত এবং যাবতীয় সামষ্টিক দায়িত্ব পালনের জন্য দায়িত্বশীল। তাঁহার বড় কর্তব্য হইল দ্বীনের যথাযথ খেদমত এবং উহার ব্যাপক প্রচার সাধন। হযরত উসমান (রা) এই দায়িত্ব পালনে সদা-সচেতন ও বিশেষ কর্তব্যপরায়ণ হইয়া থাকিতেন। প্রত্যক্ষ জিহাদে যে সব অমুসলিম বন্দী হইয়া আসিত, তাহাদের সম্মুখে তিনি নিজে দ্বীনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও উহার সৌন্দর্য প্রকাশ করিতেন এবং দ্বীন-ইসলাম কবুল করার জন্য তাহাদিগকে আহ্বান জানাইতেন। ইহার ফলে শত শত লোক ইসলাম গ্রহণ করিয়া মুসলিম সমাজের অন্তর্ভুক্ত হইবার বিপুল সুযোগ লাভ করে।
বিধর্মীদের নিকট ইসলাম প্রচার ছাড়াও স্বয়ং মুসলিম জনগণের ধর্মীয় শিক্ষা-দীক্ষার জন্যও তিনি ব্যাপক ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন। দ্বীন সংক্রান্ত জরুরী মসলা-মাসায়েল তিনি নিজেই জনগণকে জানাইয়া দিতেন। কোন বিষয়ে দ্বীনের হুকুম তাঁহার নিকট অস্পষ্ট থাকিলে অন্যান্য বিশেষজ্ঞ সাহাবীদের নিকট তিনি জিজ্ঞাসা করিয়া লইতেন ও তদনুযায়ী আমল করিতেন এবং লোকদিগকেও তাহা অনুসরণ করিয়া চলিবার জন্য নির্দেশ দিতেন। এই ব্যপারে তিনি কোনোরূপ দ্বিধা-সংকোচের প্রশ্রয় দিতেন না।
প্রয়োজনে তাগিদে ইসলামের মূল বিধানের উপর নির্ভর করিয়া নবতর ব্যবস্থা প্রবর্তন করিতেও হযরত উসমান(রা) দ্বিধা করিতেন না। মদীনার লোকসংখ্যা যখন বিপুলভাবে বৃদ্ধি পাইল, তখন মসজিদের অভ্যন্তরে ইমামের সম্মুখে জুম’আর নামাযের একটি মাত্র আযানই যথেষ্ট মনে হইল না। এই কারণে তিনি উহার পূর্বে এক উচ্চস্থানে দাঁড়াইয়া জুমায়ার আর একটি আযান দেওয়ার ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন।
এই পর্যায়ে হযরত উসমান (রা)-এর বড় অবদান হইল কুরআন মজীদকে সর্বপ্রকার মতবিরোধ ও বিকৃতি হইতে চিরকালের জন্য সুরক্ষিত করিয়া তোলার এক অতুলনীয় কার্যক্রম। আর্মেনিয়া ও আযারবাইজান অভিযানে মিশর, সিরিয়া, ইরাক প্রভৃতি অঞ্চলের মুজাহিদগণ একত্রিত হইয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই নও-মুসলিম, অনারব বংশোদ্ভুত এবং আরবী ভাষায় অনভিজ্ঞ ছিলেন। হযরত হুজাইফা ইবনে ইয়ামান (রা)-ও এই জিহাদে শরীক ছিলেন। তিনি নিজে এই দুই জিহাদে অংশ গ্রহণকারী মুসলিম মুজাহিদদের কুরআন পাঠের ধরণ ও ভঙ্গিতে মারাত্মক রকমের পার্থক্য ও বৈষম্য লক্ষ্য করিলেন। দেখা গেল, প্রত্যেক এলাকার লোকেরা নিজস্ব ইচ্ছানুসারে কুরআন পড়ে এবং উহাকেই কুরআন পড়ার একমাত্র ধরণ ও ভঙ্গী মনে করিয়া লইয়াছে। যুদ্ধ শেষে তিনি মদীনার উপস্থিত হইয়া খলীফা হযরত উসমান (রা)-এর নিকট সমস্ত ব্যাপার বিস্তারিতভাবে পেশ করিলেন। তিনি গভীর আশংকা প্রকাশ করিয়া বলিলেন, অনতিবিলম্বে এই বিরোধ ও পার্থক্য সম্পূর্ণ দূরীভূত করিয়া এক অভিন্ন ধরণ ও ভঙ্গীতে কুরআন পাঠের ব্যবস্থা করা না হইলে মুসলিম সমাজও খৃস্টান রোমানদের ন্যায় আল্লাহ্র কিতাবের ব্যাপারে নানা বিভেদ ও বিসম্বাদের সৃষ্টি করিয়া ছাড়িবে। হযরত হুযাইফা(রা)-এর দৃষ্টি আকর্ষণে হযরত উসমান (রা) ইহার প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে বুঝিতে পারিলেন। তিনি উম্মুল মু’মিনীন হযরত হাফসা (রা)-এর নিকট হইতে কুরআন মজীদের মূল গ্রন্থ আনাইয়া হযরত জায়েদ ইবনে সাবিত (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জুবাইর (রা) ও হযরত সায়াদ ইবনুল আ’স(রা) কর্তৃক উহার বহু সংখ্যক কপি তৈয়ার করাইয়া বিভিন্ন মুসলিম অঞ্চলে পাঠাইয়া দিলেন এবং উহাকেই কুরআন মজীদের চূরান্তরুপ হিসাবে গ্রহণ ও অনুসরণ করার জন্য সর্বসাধারণকে নির্দেশ দিলেন। সেই সঙ্গে লোকদের ব্যক্তিগতভাবে লিখিয়া লওয়া কুরআনের সব কপি তিনি নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলিলেন।
বস্ততঃ হযরত উসমান (রা) যদি এই পদক্ষেপ গ্রহণ না করিতেন, তাহা হইলে তওরাত, ইনজিল ও অন্যান্য আসমানী গ্রন্থের ব্যাপারে উহাদের প্রতি বিশ্বাসী লোকেরা যে মারাত্মক ধরণের মতভেদ ও বৈষম্যে নিমজ্জিত হইয়াছে, শেষ নবীর উম্মতরাও অনুরূপ বিভেদ ও বৈষম্যে পড়িয়া যাইত এবং কুরআন মজীদেরও অনুরূপ দুর্দশা ঘটিত, ইহাতে একবিন্দু সন্দেহের অবকাশ নাই। তাই ইসলামের ইতিহাসে হযরত উসমান (রা)-এর এই মহান কীর্তি চিরকাল স্বর্ণক্ষরে লিখিত থাকিবে।
হযরত আলী (রা)-এর জীবন ও চরিত্র বৈশিষ্ট্য
প্রাথমিক জীবন
হযরত আলী (রা) বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর আপন চাচাতো ভাই ছিলেন। নবী করীম (স)-এর নবুয়্যাত লাভের বৎসর হযরত আলীর বয়স হইয়াছিল মাত্র দশ বৎসর। তাঁহার পিতা আবূ তালিব বহু সংখ্যক সন্তানের পিতা ছিলেন। আর্থিক অনটন ও দুর্ভিক্ষজনিত পরিস্থিতির দরুণ দারিদ্রের দুর্বহভারে তিনি ন্যুব্জ হইয়া পরিয়াছিলেন। এই অবস্থা দেখিয়া নবী করীম (স) তাঁহার অপর চাচা হযরত আব্বাস (রা)-এর সঙ্গে আবূ তালিবের দৈন্যভার লাঘব করার উপায় সম্পর্কে পরামর্শ করেন। নবী করীম (স) তাঁহাকে বলিলেন, ‘চাচার দারিদ্র্য ও দুঃখ-কষ্ট আমাদের সমভাগে ভাগ করিয়া লওয়া উচিত’। এই পরামর্শ অনুসারে হযরত আব্বাস (রা) আবূ তালিব পুত্র জাফরের এবং নবী করীম (স) স্বয়ং হযরত আলীর লালন-পালনের সমস্ত দায়িত্ব নিজ স্কন্ধে তুলিয়া লইলেন।
বস্তুত নবী করীম (স)-এর প্রতি আবূ তালিবের অবদান ছিল অনন্য। তিনি বনু হাশিমের সরদার ছিলেন এবং সমস্ত কুরাইশ গোত্রের উপর বনু হাশিমের প্রাধান্য ও প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল অসামান্য। কা’বা ঘরের সেবা ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং তৎসংক্রান্ত যাবতীয় দায়-দায়িত্ব বনু হাশিমের উপর অর্পিত ছিল। এই কারণে তদানীন্তন আরব সমাজে আবূ তালিবের প্রাধান্য ও নেতৃত্ব এক স্থায়ী ব্যবস্থা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। সমগ্র আরবের ধর্মীয় নেতৃত্ব এই পরিবারের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিল। নবী করীম (স) জন্মের পূর্বেই ইয়াতীম হইয়া গিয়াছিলেন। ফলে জন্মের অত্যল্পকাল পর হইতেই তিনি চাচা আবূ তালিবের স্নেহময় ক্রোড়ে লালিত-পালিত হইয়া যৌবনে পদার্পণ করেন। নবুয়্যাত লাভের পর তাহাঁরই প্রবল সমর্থনে ও আশ্রয়ে তিনি তওহীদের দাওয়াত প্রচারে ব্রতী হন। অতঃপর কুফরী শক্তির পক্ষ হইতে আসা অত্যাচার-নিপীড়নের প্রতিটি আঘাতের সম্মুখে আবূ তালিব বুক পাতিয়া দেন এবং এইভাবেই কাফিরদের আক্রমণের মুকাবিলায় তিনি ভ্রাতুষ্পুত্রকে রক্ষা করেন। তাঁহার এই সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষকতার দরুণ মুশরিক কুরাইশরা গোটা আবূ তালিব বংশের সহিত চরম শত্রুতায় মাতিয়া উঠে এবং যত উপায়ে সম্ভব তাহাদিগকে জুলুম, নির্যাতন ও নিপীড়নে জর্জরিত করিয়া তোলে। তাহাদের জুলুম-অত্যাচারের এক চূড়ান্ত রূপ দেখা গিয়াছে তখন, যখন মক্কার সমস্ত মুশরিকরা সম্মিলিতভাবে এই পরিবারটির সঙ্গে সকল প্রকার সম্পর্ক ছিন্ন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং শেষাবধি এই পরিবারটি পর্বত-গুহায় আশ্রয় লইতে বাধ্য হয়। কিন্তু সত্যের পৃষ্টপোষক এই পরিবারটির নেতা ও সরদার আবূ তালিব বিন্দুমাত্র দমিত না হইয়া সকল প্রকার বিরুদ্ধতা ও নির্যাতন নীরবে মাথা পাতিয়া নেন।
ইসলাম গ্রহণ
এই আবূ তালিবের পুত্র হযরত আলী (রা) বাল্যকাল হইতেই নবী করীম (স)-এর সঙ্গী-সাথী ও সহচর হিসাবে পরিচিত হইয়া উঠেন। এই কারণে নবুয়্যাত লাভের পর রাসূলে করীমের (স)-এর জীবনে পরিবর্তন সূচিত হওয়ার বিস্ময়কর দৃশ্যাবলী তিনি নিজ চক্ষে প্রত্যক্ষ করার সুযোগ লাভ করেন। এই পরিবর্তন সম্পর্কে হযরত আলী (রা)ই জিজ্ঞাসার জবাবে নবী করীম (স) যখন তাঁহার নিকট তওহীদী দ্বীনের ব্যাখ্যা করেন এবং ইহার প্রতি ঈমান আনার আহ্বান জানান, তখনি তিনি দ্বিধাহীন চিত্তে ও উদ্দীপিত হৃদয়ে দ্বীন-ইসলামের প্রতি ঈমান আনেন।
রাসূলে করীম (স)-এর প্রতি সর্বপ্রথম কে ঈমান আনিয়াছেন, এই পর্যায়ে বহু লোকের নাম হাদীসের গ্রন্থাবলীতে উল্লেখিত হইয়াছে। মুসলিম মনীষীদের শেষ সিদ্ধান্ত এই যে, বালক বয়সের যে কয়জন লোক প্রথম ঈমান আনিয়াছিলেন, হযরত আলী (রা) তাঁহাদের মধ্যে সর্বপ্রথম ব্যক্তি।
ইসলাম কবুল করার পর হযরত আলী (রা)-র জীবনের তেরটি বৎসর মক্কা শরীফে রাসূলে করীম (স)-এর গভীর সান্নিধ্যে অতিবাহিত হইয়াছে। তিনি যেহেতু সর্বক্ষণ রাসূলে করীম (স)-এর সঙ্গে থাকিতেন, এইজন্য পরামর্শ সভা, শিক্ষা-দীক্ষার মজলিস, কাফির মুশরিকদের সহিত বিতর্ক বৈঠক এবং এক আল্লাহ্র ইবাদাতের অনুষ্ঠানাদি-এক কথায় সর্ব ব্যাপারে তিনি রাসূলে করীম (স)-এর সহিত শরীক থাকিবার অফুরন্ত সুযোগ লাভ করেন। নবী করীম (স)নবুয়্যাতের প্রাথমিক পর্যায়ে যখন অতীব গোপনে ও লকচক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া এক আল্লাহ্র বন্দেগীতে নিমগ্ন হইতেন, হযরত আলী (রা) তাহাতেও উপস্থিত থাকিবার সুযোগ পাইতেন। এই গোপনীয়তা সত্ত্বেও আবূ তালিব একবার পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রকে বিশেষ ধরণের ইবাদতে মশগুল দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেনঃ ‘তোমরা দুইজন কি করিতেছ? তখন নবী করীম (স) তওহীদী দ্বীন ও আল্লাহ্র ইবাদতের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। আবূ তালিব সবকিছু শুনিয়া বলিলেনঃ ‘ঠিক আছে, ইহাতে কোন দোষ নাই। তোমরা করিতে পার; কিন্তু আমার পক্ষে সম্ভব হইবে না’।
নবুয়্যাত লাভের পর ক্রমাগত তিনটি বৎসর পর্যন্ত নবী করীম (স) দ্বীন-ইসলামের প্রকাশ্য দাওয়াত পেশ হইতে বিরত থাকেন। এই সময় দ্বীন প্রচারের সমস্ত কাজ তিনি বিশেষ গোপনীয়তা সহকারে চালাইতে থাকেন। তিনি বিশেষ লোকদের নিকট দ্বীনের দাওয়াত পেশ করার সঙ্গে সঙ্গে দ্বীনী আদর্শানুযায়ী লোকদের মন-মানসিকতা ও চরিত্র গঠনের দায়িত্বও পালন করিতেন। চতুর্থ বৎসর তাঁহার প্রতি আল্লাহ্ তা’আলার নির্দেশ অবতীর্ণ হইলঃ
******(আরবী)
তোমার বংশের নিকটবর্তী পূর্ণসংখ্যক লোকদিগকে (বেঈমানি ও শিরকের পরকালীন আযাব সম্পর্কে ) ভীত ও সাবধান করিয়া তোল।
নবী করীম (স) আল্লাহ্ তা’আলার এই নির্দেশ লাভ করিয়া নিকটবর্তী ‘সাফা’ পর্বতের চূড়ায় উঠিলেন এবং নিজ বংশের বিপুল জনতার সম্মুখে সর্বপ্রথম তওহীদী দ্বীনের আহবান উদাত্ত কণ্ঠে পেশ করিলেন। ইহার পরও নবী করীম (স) নিজের পরিবার ও বংশের লোকজনের নিকট সত্য দ্বীনের প্রতি ঈমান আনার দাওয়াত পেশের জন্য নানাভাবে প্রচেষ্টা চালাইয়াছেন। এমন কি একবার এই উপলক্ষে একটি ভোজের আয়োজন করার জন্য তিনি হযরত আলী (রা)-কে নির্দেশ দেন।
দ্বীন প্রচারে সহযোগিতা
হযরত আলী (রা)র বয়স তখন খুব বেশী হইলেও চৌদ্দ পনের বৎসরের অধিক হইবে না। কিন্তু এই অল্প বয়স সত্ত্বেও তিনি বিশেস দক্ষতা সহকারে নিজ বংশ ও পরিবারের লোকদের জন্য এক বিরাট ভোজের আয়োজন করেন। সংশ্লিষ্ট সমস্ত লোকই ভোজসভায় উপস্থিত হয়। প্রায় চল্লিশজন লোক ইহাতে যোগদান করে। কুরাইশ বংশের প্রভাবশালী প্রায় সব কয়জন সরদারই এখানে সমবেত হয়। খাওয়া-দাওয়া শেষ হইবার পর নবী করীম (স) দাঁড়াইয়া এক সংক্ষিপ্ত ভাষণের মাধ্যমে উপস্থিত জনগণের দ্বীন-ইসলাম কবুল করার আহবান জানান। আল্লাহ্ তা’আলা তাঁহার উপর দ্বীন প্রচারের যে বিরাট দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছেন, সেই কাজে তাঁহার সহিত সহযোগিতা করিবার জন্য তিনি প্রসঙ্গত সকলেই উদ্ধুদ্ধ করিতে চেষ্টা করেন। নবী করীম (স)-এর ভাষণ শেষে সভাস্থলে সর্বপ্রথম হযরত আলী (রা)র কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হইয়া উঠে। তিনি নির্ভীক কণ্ঠে বলিয়া উঠেনঃ ‘বয়সে আমি ছোট। দৈহিক অক্ষমতাও আমার অবর্ণনীয়। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও আমি এই মহান ব্রতে আপনার সঙ্গী, চির সহচর ও প্রান-পণ সাহায্যকারী থাকিব’। তাঁহার এই কথা শুনিয়া নবী করীম (স) বলিলেনঃ ‘তুমিই আমার ভাই ও আমার উত্তরাধিকারী’।
নবুয়্যাতের প্রায় তেরটি বৎসর মক্কায় অতিক্রান্ত হওয়ার পর আল্লাহ তা’আলা নবী করীম (স)-কে সমস্ত মুসলমান সমভিব্যাহারে মদীনায় হিজরাত করিয়া যাইবার জন্য নির্দেশ দেন। সে অনুসারে নবী করীম (স) মক্কার মুসলমানদিগকে একের পর এক মদীনায় চলিয়া যাইতে বলিলেন। ইহাতে মক্কা শহর মুসলমান-শূন্য হইয়া পড়ার আশংকা দেখা দিল। এই অবস্থা দেখিয়া কাফির মুশরিকগণ বিশেষভাবে শংকিত ও ভীত হইয়া পড়ে এই ভাবিয়া যে, মুসলমানরা বাহিরে কোথাও সংঘবদ্ধ ও বিপুল শক্তিতে বলীয়ান হইয়া আমাদের উপর আক্রমন করিয়া বসিতে পারে। এই আশংকায় তাহারা আগে-ভাগেই ‘শত্রু’ নিধনে কৃত-সংকল্প হইল। আল্লাহ্ তা’আলা অহীর মাধ্যমে নবী করীম (স)-কে এই বিষয়ে যথাসময়ে অবহিত করিলেন এবং অনতিবিলম্বে হিজরাত করার জন্য আদেশ দিলেন। তিনি হযরত আলী (রা)কে নিজের শয্যায় শায়িত রাখিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া যান এবং হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) সমভিব্যাহারে মদীনার দিকে রওয়ানা হন।
কাফির মুশরিকরা নবী করীম (স)-কে হত্যা করিয়া ইসলামের প্রোজ্জ্বল সূর্যের চির অস্তগমনের ব্যবস্থা করার জন্য সারা রাত্রব্যাপী তাঁহার বাসগৃহ অবরুদ্ধ ও পরিবেষ্টিত করিয়া রাখে। হযরত আলী (রা) তখন বাইশ-তেইশ বৎসরের এক যুবক মাত্র। তিনি কাফিরদের মারাত্মক ষড়যন্ত্র সম্পর্কে অবহিত হওয়া সত্ত্বেও অসীম সাহসিকতা সহকারে রাসূলের শয্যায় নিশ্চিন্তে ঘুমাইয়া থাকেন। সকাল বেলা শত্রুবাহিনী ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখিতে পায়, রাসূলে করীম (স) অনুপস্থিত এবং তাহাঁরই জন্য প্রান-উৎসর্গকারী এক যুবক তাহাঁরই শয্যায় আত্মদানের দৃঢ় সঙ্কল্প লইয়া নিদ্রায় অচেতন হইয়া রহিয়াছে। তখন তাহারা নিজেদের এই সম্মিলিত অভিযানের চূড়ান্ত ব্যর্থতা এবং রাসূলে করীম (স)-এর অবধারিত সাফল্য বুঝিতে পারিয়া মর্মাহত, লজ্জিত ও হতাশাগ্রস্ত হইয়া পড়ে।
মদীনায় কর্মময় জীবন
ইহার পর হযরত আলী (রা) দুই বা তিন দিন পর্যন্ত মক্কায় অবস্থান করেন। রাসূলে করীম (স)-এর নির্দেশ অনুযায়ী তাঁহার নিকট রক্ষিত জনগণের আমানতসমূহ যথাযথভাবে প্রত্যার্পণের পর তিনিও মক্কা ত্যাগ করিয়া মদীনা অভিমুখে যাত্রা করেন।
মদীনায় উপস্থিত হওয়ার পর সর্বপ্রথম মসজিদে নববীর নির্মাণে হযরত আলী (রা) প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করেন। তিনি রাসূলে করীম (স)-এর নির্দেশ অনুযায়ী উহার ভিত্তি স্থাপন করেন এবং অন্যান্য সঙ্গী-সাথীদের সহিত একত্র হইয়া উহার নির্মাণ কার্য সুসম্পন্ন করিয়া তোলেন।
অতঃপর বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর সুকঠিন কর্মময় জীবন শুরু হইলে হযরত আলী (রা) সেই ক্ষেত্রে ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও অদম্য সাহসিকতা সহকারে ছায়ার মতই তাঁহার সঙ্গী হইয়া থাকেন। নবী করীম (স)-এর প্রায় সব কয়টি যুদ্ধ-জিহাদেই তিনি পূর্ণ দায়িত্ব লইয়া অংশ গ্রহণ করেন। এসব ক্ষেত্রে তিনি যে বীরত্বের পরিচয় দিয়াছেন, উহাতে তাঁহার সমকক্ষ আর কেহই হইতে পারে না। বদর যুদ্ধে নবী করীম (স) তিনশত তের জন জীবন-উৎসর্গকারী সাহাবী সমভিব্যাহারে মদীনা হইতে রওয়ানা হইলেন। কাফেলার সম্মুখভাবে কালো বর্ণের দুইটি পতাকা মুসলিম বাহিনীর অগ্রাভিযানের নিদর্শন স্বরূপ পতপত করিয়া উড়িতেছিল। উহার একটি পতাকা হযরত আলী (রা)র হস্তে উড্ডীন হইতেছিল। বদর নামক স্থানে উপস্থিত হওয়ার পর নবী করীম (স) শত্রুপক্ষের গতি-বিধি লক্ষ্য করার উদ্দেশ্যে হযরত আলী (রা)র নেতৃত্বে একটি দুঃসাহসী ঝটিকা বাহিনী প্রেরণ করেন। ওহোদ যুদ্ধে নবী করীম (স) আহত হইয়া একটি গর্তে পড়িয়া গেলে শত্রু বাহিনীর লোকেরা তাঁহার দিকে তীব্র গতিতে অগ্রসর হয়। এই সময় প্রথমে হযরত মুসয়াব ইবনে উমাইর (রা) তাহাদের সহিত লড়াই করিতে করিতে শাহাদাত বরণ করেন। তাঁহার পরই হযরত আলী (রা) অগ্রসর হইয়া পতাকা ধারণ করেন এবং প্রতিরোধ যুদ্ধে বীরত্বের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া যুদ্ধের মোড় ঘুরাইয়া দেন।
বনু কুরাইজা অভিযানেও হযরত আলী (রা)র হস্তেই পতাকা উড়িতেছিল এবং রাসূলে করীম (স)-এর নির্দেশ অনুযায়ী ইয়াহুদীদের দুর্গ দখল করার পর উহার প্রাঙ্গনে তিনি আসরের নামায পড়েন। হুদাইবিয়ার হযরত উসমান (র)-এর শাহাদাতের সংবাদ পাওয়ার পর সাহাবীদের নিকট হইতে আত্মোৎসর্গ করার যে বায়’আত গ্রহণ করা হয়, হযরত আলী (রা)ও এই বায়’আতে শরীক ছিলেন। পরে মক্কার মুশরিকদের সহিত যে সন্ধি-চুক্তি লিখিত ও সাক্ষরিত হয়, নবী করীম (স) উহা লিখিবার জন্য তাঁহাকেই নির্দেশ দেন। খায়বর যুদ্ধে প্রথম দুইটি অভিযানে নেতৃত্ব দেন হযরত আবূ বকর (রা) ও হযরত উমর (রা)। কিন্তু কোন অভিযানেই বিজয় সম্ভবপর হয় নাই। সর্বশেষে নবী করীম (স) হযরত আলী (রা)র স্কন্ধে খায়বরের দুর্ভেদ্য দুর্গসমূহ জয় করার দায়িত্ব অর্পণ করেন। তিনি প্রবল বিক্রমে যুদ্ধ করিয়া খায়বরের দুর্গসমূহের উপর ইসলামের বিজয় পতাকা উড্ডীন করেন। মক্কা বিজয়ের অভিযানেও তিনি অগ্রবর্তী বাহিনীর পতাকা লইয়া বিজয়ীর বেশে নগর অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন। তাবুক যুদ্ধ হইতে প্রত্যাবর্তনের পর নবী করীম (স) সেই বৎসরের হজ্জে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-কে ‘আমীরে হজ্জে’ বানাইয়া মক্কায় প্রেরণ করেন। তাঁহার রওয়ানা হইয়া যাওয়ার পর সূরা ‘বারায়াত’(তওবা) নাযিল হয়। মদীনায় উপস্থিত সাহাবীগণ এই সূরাটি আদ্যোপান্ত শুনার পর মত প্রকাশ করেন যে, হজ্জের সময় সমবেত মুসলমানদের সম্মুখে এই সূরাটি পড়িয়া শুনানো হইলে খুবই ভালো হইবে। নবী করীম (স)ও ইহার গুরুত্ব অনুধাবন করিয়া হযরত আলী (রা)কে এই দায়িত্ব দিয়া মক্কা শরীফ পাঠাইয়া দিলেন।
ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে নবী করীম (স) যে কয়টি প্রতিনিধিদল বিভিন্ন অঞ্চলে প্রেরণ করেন, ইয়েমেনে প্রতিনিধিদল প্রেরণ তন্মধ্যে বিশেষ গুরুত্তের অধিকারী। হযরত খালিদ ইবনে অলীদ (রা) দীর্ঘ ছয় মাস যাবত নানাভাবে চেষ্টা চালাইয়াও সফলকাম হইতে ব্যর্থ হন সর্বশেষে হিজরী দশম বৎসরে নবী করীম (স) হযরত আলী (রা)-কে এই দায়িত্ব দিয়া পাঠাইবার সিদ্ধান্ত নেন। হযরত আলী (রা) ইয়েমেন উপস্থিত হইতেই সেখানকার অবস্থার আমূল পরিবর্তন সূচিত হয়। তিনি সেখানকার লোকদের সম্মুখে ইসলামের তত্ত্ব,মাহাত্ম্য ও বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করেন এবং ইহার ফলে হাজার হাজার লোক ইসলাম দীক্ষিত হন।
একাদশ হিজরীর রবীউল আউয়াল মাসে নবী করীম (স) পরলোক গমন করেন। এই মর্মান্তিক বেদনা সমস্ত মুসলিম জগতকে প্রচণ্ডভাবে ব্যথাতুর করিয়া ফেলে। নবী পরিবারের সদস্যগণ সর্বাধিক পরিমাণে কাতর ও বেদনা-বিধুর হইয়া পড়েন। প্রত্যেকেরই হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়, চক্ষুদ্বয় চিরকালের জন্য শ্রাবণের অস্রু নির্ঝরে পরিণত হয়। হযরত আলী (রা) নবী পরিবারের মধ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব ছিলেন। ব্যক্তিগত সম্পর্কও ঘনিষ্ঠতার দিক দিয়া যেমন, পারিবারিক ও আত্মীয়তার দিক দিয়াও তেমনি এই বেদনা তাঁহার পক্ষে অসহনীয় হইয়াছিল। তদুপরি নবী-তনয়া হযরত ফাতিমা (রা)র ইয়াতীমী তাঁহা অন্তরে দুঃসহ আঘাত হানে। তিনি ভয়ানক রকম মুষড়িয়া পড়েন এবং দীর্ঘ দিন পর্যন্ত সমাজ ও রাষ্ট্রের সহিত সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া নিতান্তই ঘর-বাসী হইয়া থাকেন। এই সময় নিজের দুঃখ সামলানো, হযরত ফাতিমা (রা)-কে সান্তনা দান এবং কুরআন মজীদ সুসংবদ্ধকরণ ব্যতীত অন্য কোন কাজের প্রতি বিন্দুমাত্র উৎসাহ বা কৌতূহল প্রদর্শন করা তাঁহার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল। কিছুদিন পর হযরত ফাতিমা (রা) ও যখন ইন্তেকাল করিয়া গেলেন তখন তিনি নিজেকে যেন নাড়া দিয়া উঠাইলেন এবং প্রথম খলীফা আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার হস্তে খিলাফতের বায়’আত করেন।
হযরত আবূ বকর (রা)-এর পরে হযরত উমর ফারুক (রা) তাঁহার খিলাফত আমলে সকল জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে হযরত আলী (রা)-এর সহিত পরামর্শ করিতেন। হযরত আলী (রা)ও তখন অত্যন্ত নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা সহকারে প্রতিটি ব্যাপারে তাঁহাকে পরামর্শ দিতেন। নিহাওয়ান্দ অভিযানে তাঁহাকে সেনাধ্যক্ষের দায়িত্ব গ্রহণের প্রস্তাব করা হয়। কিন্তু তিনি তাহা গ্রহণ করিতে অসম্মত হন। পরে উমর (রা) যখন বায়তুল মাকদিস গমন করেন, রাজধানীতে হযরত আলী (রা)কে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত (Acting)করিয়া খিলাফতের সমস্ত দায়িত্ব তাঁহার নিকট অর্পণ করিয়া যান। হযরত উমর (রা)-এর পর হযরত উসমান (রা)-এর খিলাফতের শেষ দিকে সারা দেশে যখন অশান্তি ও উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা দেয়, তখন তাহা দমন করার জন্য হযরত আলী (রা) বিশেষ ও কার্যকর পরামর্শ দান করেন এবং অশান্তির মূল কারণসমূহ নির্দেশ করিয়া তাহা সংশোধন ও বিদূরণের পন্থা দেখাইয়া দেন।
হযরত আলী (রা)-র খিলাফত
খলীফা নির্বাচন
হযরত উসমান (রা)-এর শাহাদাত বরণের পর তিনদিন পর্যন্ত খিলাফতের আসন শূন্য থাকে। এই সময় পরবর্তী খলীফার জন্য হযরত আলী (রা)-এর প্রতি জনগণের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়। বহু লোক তাঁহাকে এই দায়িত্ব গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানায়। প্রথম দিকে তিনি স্পষ্ট ভাষায় অসম্মতি জানানো সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত মুহাজির ও আনসার সাহাবীগণের পৌনঃপুনিক অনুরোধে এই দায়িত্ব গ্রহন করিতে তিনি সম্মত হন।
হযরত আলী (রা)-এর খলীফা নির্বাচিত হওয়ার বিবরণ ইসলামী রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ইতিহাসে সবিস্তারে উল্লেখিত হইয়াছে। জনতা হযরত আলী (রা)র নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলঃ
*******(আরবী)
আমরা আপনার হাতে আনুগত্যের বায়’আত করিব, আপনি হাত প্রসারিত করিয়া দিন। কেননা এখন আমাদের একজন আমীর-রাষ্ট্রনায়ক-নিযুক্ত করা একান্তই অপরিহার্য। আর এই পদের জন্য আপনি অধিকতর যোগ্য ও অধিকারী।
হযরত আলী (রা) ইহার উত্তরে বলিলেনঃ
*******(আরবী)
এই ব্যাপারে কিছু বলার বা করার তোমাদের কোন অধিকার নাই। ইহাতো পরামর্শদানের যোগ্যতাসম্পন্ন ও বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী প্রাথমিক পর্যায়ের মুসলমানদের সম্মিলতভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপার। তাঁহারা যাহাকে খলীফারূপে গ্রহণ করিবেন, তিনিই খলীফা হইবেন। অতএব চল, আমরা সকলে একত্রিত হই এবং বিষয়টি সম্পর্কে বিচার-বিবেচনা করি।
এই কথা শুনিয়া লোকেরা তাঁহার নিকট হইতে চলিয়া গেল। কিন্তু কিছুক্ষন পর তাহারা পুনরায় তাঁহার নিকট আসিয়া বায়’আত করার জন্য চাপ দিতে থাকে। তখন হযরত আলী (রা) বলিলেনঃ
******(আরবী)
তোমরা যদি ইহাই চাও যে, ‘আমি খলীফা হই ও তোমাদের নিকট হইতে আনুগত্যের বায়’আত গ্রহণ করি, তাহা হইলে মসজিদে নববীতে চল,সেখানেই এই বিষয়ে চূড়ান্ত ফয়সালা হইবে।
নিশ্চিন্ত কথা, আমাকে খলীফা নির্বাচন করা ও সেজন্য আনুগত্যের বায়’আত করা গোপনে অনুষ্ঠিত হইতে পারে না। ইহা অবশ্যই মুসলিম জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত সন্তোষ ও অনুমোদনের ভিত্তিতেই হইতে পারে।
অতঃপর মসজিদে নববীতে সমবেত সর্বসাধারণ মুসলমানদের প্রস্তাবনা এবং স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন ও আনুমোদনের পর হযরত আলী (রা)-কেই পরবর্তী খলীফা নির্বাচিত করা হয় এবং ২১ শে যিলহজ্জ সোমবার দিন মসজিদে নববীতে বিপুল ইসলামী জনতার উপস্থিতিতে তাঁহারই হস্তে খিলাফতের সাধারণ বায়আত গ্রহণ করা হয়। তিনি বরিত হন খিলাফতে রাশেদার চতুর্থ খলীফা হিসাবে।
হযরত আলী (রা) যখন খিলাফতের দায়িত্ব নিজের স্কন্ধে তুলিয়া নেন, তখন সমগ্র মুসলিম জাহান চরম অরাজকতা ও বিদ্রোহ-বিপ্লবের লীলাভূমিতে পরিণত হইয়াছিল। প্রথম খলীফা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) কেও অনুরূপ এক অশান্তি ও বিদ্রোহ-বিপ্লবের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল বটে; কিন্তু এই দুইটি অবস্থার মধ্যে বিরাট পার্থক্য ছিল। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)কে যে বিপদের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল,তাহা ছিল কাফিরী ও ইসলামত্যাগী এবং ইসলামের পারস্পরিক সংঘর্ষ। সমস্ত ইসলামী জনতা এই সংঘর্ষের খলীফার সমর্থক ও পৃষ্ঠপোষক ছিল। বিরুদ্ধবাদীরা ছিল বাতিলপন্থী,লালসা ও দুস্প্রবৃত্তির অনুসারী। তাহাদের মতের কোন স্থিতি বা দৃঢ়তা ছিল না। পক্ষান্তরে হযরত আলী (রা) কে যাঁহাদের বিরুদ্ধতার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল, তাঁহারা শুধু মুসলমানই ছিলেন না, বহু সংখ্যক সাহাবী এবং রাসূলে করীম (স)-এর সহধর্মিণী হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) পর্যন্ত তাঁহাদের মধ্যে শামিল ছিলেন। ইহাকে ভাগ্যের চরম পরিহাস ছাড়া আর কি-ইবা বলা যাইতে পারে।
কিন্তু এইসব বিপদ-আপদ, অশান্তি-উপদ্রব ও বিদ্রোহ-বিপ্লব সত্ত্বেও হযরত আলী(রা) অত্যন্ত দৃঢ়তা ও দুঃসাহসিকতা সহকারে খিলাফত তরুণীর হাল শক্ত করিয়া ধরিয়া রাখেন। এই সময় তিনি অপরিসীম ধৈর্য-সহিষ্ণুতা ও সুস্থ চিন্তা-বিবেচনার চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন এবং নানাক্ষেত্রে ব্যর্থতার নিদর্শন লক্ষ্য করা সত্ত্বেও পরম বিশ্বাসপরায়ণতা, অবিচল আদর্শবাদিতা এবং ইসলামী শরীয়াত ও রাষ্ট্রনীতির মৌল বিধান হইতে বিন্দুমাত্র বিচ্যুতিও সহ্য করিতে সম্মত হন নাই। তিনি যদি নীতি ও আদর্শবাদ হইতে একচুল পরিমাণ বিচ্যুতিও সহ্য করিতে প্রস্তুত হইতেন, তাহা হইলে রাষ্ট্রনীতির বিচারে তিনি হয়ত সফলকাম বিবেচিত হইতেন;কিন্তু দ্বীন-ইসলামের মহান আদর্শ ক্ষুণ্ণ,বর্জিত ও পরিত্যক্ত হইত, ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই। অথচ ইহাকে রক্ষা করাই হইল খলীফায়ে রাশেদ ও রাসূলে করীম (স)-এর স্থলাভিষিক্তের সর্বপ্রথম ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।
খলিফারুপে হযরত আলী (রা)
খিলাফতের শাসন-ব্যবস্থা পরিচালনায় হযরত আলী (রা) হযরত উমর ফারুক (রা)-এর পদাংক অনুসরণের কৃত-সংকল্প ছিলেন এবং তৎকালে প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থাপনায় কোনোরূপ মৌলিক পরিবর্তন সাধনে কিছুমাত্র সম্মত ছিলেন না। হযরত উমর ফারুক (রা) সমগ্র হিজাজ হইতে নির্বাসিত যেসব ইয়াহুদীকে নাজরান নামক স্থানে পুনর্বাসিত করিয়াছিলেন, তাহারা হযরত আলী (রা)র নিকট উপস্থিত হইয়া অত্যন্ত কাতর ও বিনীত কণ্ঠে তাহাদের প্রাক্তন বসতিতে প্রত্যাবর্তনের অনুমতি প্রার্থনা করে। কিন্তু হযরত আলী (রা) ইহাতে স্পষ্ট ভাষায় অস্বীকৃতি জানাইয়া বলিলেনঃ ‘হযরত উমর (রা) অপেক্ষা অধিক সুবিবেচক, বিচক্ষণ এবং সঠিক সিদ্ধান্তকারী আর কে হইতে পারে’?
দেশের আভ্যন্তরীণ শাসন-ব্যবস্থায় সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ হইল, দায়িত্বশীল কর্মকর্তাদের নিয়ন্ত্রণ এবং তাহাদের কার্যাবলী ও আচার-ব্যবহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ। হযরত আলী (রা) এই বিশেষ বিষয়টির উপর সব সময় দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিতেন। তিনি কোন দায়িত্বপূর্ণ পদে কাহাকেও নিয়োগ দান করার সময় অতীব মূল্যবান ও কল্যাণময় উপদেশাবলী প্রদান করিতেন। ইহা ছাড়া বিভিন্ন সময়ে এইসব কর্মকর্তাদের কার্যাবলী ও আচার-ব্যবহার সম্পর্কে বিশেষভাবে তদন্ত করাইতেন। এই গুরুত্বপূর্ণ কাজে একবার হযরত কায়াব ইবনে মালিক (রা) কে নিযুক্ত করিয়া নিম্নোক্ত ভাষায় তাঁহাকে নির্দেশ দিলেনঃ
********(আরবী)
তুমি তোমার সঙ্গীদের একটি দল লইয়া রওয়ানা হইয়া যাও এবং ইরাকের প্রতিটি জিলায় ঘুরিয়া ফিরিয়া কর্মচারীদের কাজকর্ম এবং তাহাদের স্বভাব-চরিত্র ও আচার-ব্যবহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য কর। তিনি সরকারী কর্মচারীদের অপচয় ও ব্যয়বাহুল্য এবং রাষ্ট্রীয় অর্থের ব্যাপারে তাহাদের অনিয়মতান্ত্রিকতা কঠোর হস্তে দমন করিতেন। বায়তুলমাল হইতে গৃহীত ঋণ যথাসময়ে আদায় করার জন্য কর্মচারীদের বিশেষভাবে কড়াকড়ি করিতেন। এই ব্যাপারে তিনি তাঁহার নিকটাত্মীয়দের প্রতি এতটুকু নমনীয়তা বা প্রীতি দেখাইতে প্রস্তুত ছিলেন না।
হযরত আলী (রা) রাজস্ব বিভাগের বিশেষ সংস্কার সাধন ও উন্নয়নমূলক নীতির প্রবর্তন করেন। রাজস্ব আদায়ে পূর্ণ কঠোরতা সত্ত্বেও সাধারণ জনগণের সার্বিক কল্যাণ ও সাধারণ অবস্থার উন্নয়ন সাধনে তিনি প্রতিনিয়ত যত্নবান ছিলেন। অক্ষম ও দরিদ্র জনতার প্রতি তিনি সব সময় অনুকম্পামূলক নীতি গ্রহণ করিতেন।
বস্তুত হযরত আলী (রা) ছিলেন জন-মানুষের জন্য আল্লাহ্র অপার রহমতের বাস্তব নিদর্শন ও জ্বলন্ত প্রতীক। তাহার খিলাফত আমলে সমাজের সাধারণ দীন-দরিদ্র ও অভাবগ্রস্ত লোকদের জন্য রাষ্ট্রীয় বায়তুলমালের দ্বার ছিল সদা উন্মুক্ত। বায়তুলমাল-এ যাহা কিছুই সঞ্চিত ও সংগৃহীত হইত, অভাবগ্রস্ত ও পাওয়ার যোগ্য লোকদের মধ্যে তাহা তিনি অনতিবিলম্বে ও উদার হস্তে বণ্টন করিয়া দিতেন। দেশের অমুসলিম নাগরিকদের সহিত তিনি অত্যন্ত সহৃদয়তা ও সহানুভূতিপূর্ন আচরণ অবলম্বন করিতেন। এমন কি, বিদ্রোহ ভাবাপন্ন ও ষড়যন্ত্রকারীদের কার্যকলাপও অতীব ধৈর্য-সহিষ্ণুতা সহকারে বরদাশত করা হইত।পারস্য অঞ্চলে খলীফার অনুসৃত এই উদার নীতির চমৎকার অনুকূল প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা গিয়াছিল।
হযরত আলী (রা) নিজে একজন সুদক্ষ ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সমর-নায়ক ছিলেন। সামরিক বিষয় ও ব্যাপারাদিতে তাঁহার দূরদর্শীতা ও বিচক্ষণতা ছিল তুলনাহীন। এই কারণে ইসলামী রাষ্ট্রের সামরিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বহু নবতর ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর হইয়াছিল।
হযরত আলী (রা)র মনীষা
হযরত আলী (রা) বাল্যকাল হইতেই নবুয়্যাতের শিক্ষা অঙ্গন হইতে সরাসরি জ্ঞান অর্জন ও প্রশিক্ষন লাভের সুযোগ পাইয়াছিল। রাসূলে করীম (স)-এর সহিত তাঁহার যে গভীরতর সম্পর্ক ও ঘনিষ্ঠতা ছিল, তাহারই দৌলতে তিনি এই পর্যায়ের অন্যান্য সকলের তুলনায় অধিক সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন। ঘরে-বাহিরে ও বিদেশ যাত্রাকালে তিনি নবী করীম (স)-এর নিবিড়তর নৈকট্য লাভ করিতে পারিয়াছিলেন বিধায় দ্বীন-ইসলামের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞানলাভ করা তাঁহার পক্ষে খুবই সহজ হইয়াছিল। নবী করীম (স) নিজেও তাঁহাকে এই বিশেষ জ্ঞান দান করার জন্য গুরুত্ব দিয়াছিলেন। তিনি নিজে তাঁহাকে কুরআন মজীদ শিক্ষা দিয়াছেন এবং কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের সঠিক তাৎপর্য বুঝাইয়া দিয়াছেন। এই কারণে অন্যান্য সাহাবায়ে কিরামের তুলনায় তাঁহার মনীষা ছিল অত্যন্ত ব্যাপক ও গভীরতর। রাসূলে করীম (স) তাঁহার এই মনীষার প্রতি ইঙ্গিত করিয়া বলিয়াছিলেনঃ
******(আরবী)
‘আমি জ্ঞানের নগরী আর আলী উহার দ্বার বিশেষ’।
একটি হাদীস হিসাবে সনদ ইত্যাদির বিচারে এই কথাটি গ্রহণযোগ্য না হইলেও ইহার বাস্তবতা অবশ্যই স্বীকৃতব্য। সাধারণ লেখাপড়া হযরত আলী (রা) বাল্যকালেই শিখিয়া লইয়াছিলেন এবং অহী লেখকদের তালিকায় তাঁহার নামও শামিল রহিয়াছেন। রাসূলে করীম (স)-এর নির্দেশ অনুযায়ী বহু রাষ্ট্রীয় ফরমানসহ হুদাইবিয়ার সন্ধিনামা হযরত আলী (রা)র হস্তেই সুলিখিত হইয়াছিল।
ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের মূল উৎস কুরআন মজীদ। হযরত আলী (রা) এই কুরআনের মহাসমুদ্র মন্থন করার সৌভাগ্য অর্জন করিয়াছিলেন। যে কয়জন সাহাবী নবী করীম (স)-এর জীবদ্দশায় পূর্ণ কুরআন মজীদ মুখস্থ করিয়া লইয়াছিলেন, হযরত আলী (রা) তাঁহাদের অন্যতম। কুরআনের কোন সূরা বা কোন আয়াতটি কি প্রসঙ্গে ও কোন সময় নাজিল হইয়াছিল, এই বিষয়ে তাঁহার বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। তিনি এই কথা নিজেই দাবি করিয়া বলিয়াছিলেন। এই কারণে কুরআনের মুফাসসিরদের উচ্চতম স্তরে তিনি পরিগণিত। উত্তরকালে রচিত বড় বড় তফসীর গ্রন্থে হযরত আলী (রা)র ব্যাখ্যামূলক বর্ণনাসমূহ বিশেষভাবে উদ্ধৃত হইয়াছে। কুরআনের মজীদকে নাজিল হওয়ার পরম্পরায় সুসজ্জিত করা তাঁহার এক বিশেষ অবদান। সেই সঙ্গে কুরআন মজীদ হইতে ব্যবহারিক জীবনের জন্য জরুরী আইন-বিধান বাহির করা এবং বিভিন্ন জটিল বিষয়ে ইসলামের নির্দেশ ও সিদ্ধান্ত জানার জন্য ইজতিহাদ কর্যা তাঁহার অসাধারণ দক্ষতা ও প্রতিভা সর্বজনস্বীকৃত। খারিজী ফির্কার লোকেরা নিতান্ত আক্ষরিক অর্থে কোন ব্যক্তিকে মীমাংসাকারী বা পারস্পরিক বিবাদ মিটাইবার জন্য মানিয়া লইতে অস্বীকৃতি জানাইল এবং তাহারা দলীল হিসাবে কুরআনের আয়াত ****(আরবী) ‘এক আল্লাহ্ ছাড়া মীমাংসাকারী আর কেহ হইতে পারে না’ পেশ করিল, তখন তিনি এইরূপ যুক্তি উপস্থাপনের অযৌক্তিকটা ও অবান্তরতা প্রমাণ করিয়া বলিলেনঃ ‘আল্লাহই যে চূড়ান্ত বিচারক তাহাতে আর সন্দেহ কি! কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক বিবাদ মিমাংসা করার জন্য আল্লাহ্ তা’আলা নিজেই যখন জনসমাজের লোককে সালিশ মানিবার জন্য নির্দেশ দিয়া বলিয়াছেনঃ
*******(আরবী)
স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের মধ্যে বিবাদ-বিরোধের আশংকা দেখা দিলে স্বামীর পক্ষ হইতে একজন এবং স্ত্রীর পক্ষ হইতে একজন মিমাংসাকারী প্রেরণ কর।
তখন মুসলিম জাতি ও জনতার পারস্পরিক বিবাদ মীমাংসার জন্য জনসমাজ হইতেই কাহাকেও নিযুক্ত করা ও মানিয়া লওয়া হইলে তাহা অন্যায় বা কুরআন-বিরোধী কাজ হইবে কেন? আল্লাহ্র সার্বভৌমত্ব ও সর্ব বিষয়ে তাঁহার চূড়ান্ত ক্ষমতা তো কোন-না-কোন মানুষের দ্বারাই কার্যকর ও বাস্তবায়িত হইবে। গোটা মুসলিম জাতির পারস্পরিক বিবাদ-বিসম্বাদের ব্যাপারটি কি একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোকের তুলনায়ও নগণ্য ব্যাপার?বস্তুতঃকুরআনের তাফসীর ও আয়াতসমূহের তাৎপর্য ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ পর্যায়ে হযরত আলী (রা)-র এত মূল্যবান বর্ণনাসমূহ উদ্ধৃত হইয়াছে যে, তাহা একত্র সন্নিবেশিত করা হইলে একখান বিরাট গ্রন্থের রূপ পরিগ্রহ করিতে পারে।
এক শ্রেণীর প্রতারক তাসাউফপন্থী প্রচার করিয়া বেড়ায় যে, রাসূলে করীম (স) হযরত আলী (রা)-কে দ্বীন-ইসলাম সংক্রান্ত মৌল জ্ঞান ও বিদ্যা ছাড়াও এমন কিছু জ্ঞানও তাঁহাকে শিক্ষা দিয়া গিয়াছিলেন যাহাকে বর্তমানে ‘তাসাউফ’ নামে অভিহিত করা হয়। তাহারা হযরত আলী (রা)-কে তাসাউফ শাস্ত্রের ‘আদি পিতা’ বলিয়াও প্রচারনা চালাইতেছে। কিন্তু ইহা কতবড় মিথ্যা অপবাদ এবং কতখানি ভিত্তিহীন কথা, তাহা একটি সহীহ হাদীসে উদ্ধৃত তাঁহার নিজের উক্তি হইতেই অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়। লোকেরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলঃ ‘আপনার নিকট কুরআন ছাড়া আরও কোন ইলম আছে নাকি?’ তিনি জওয়াবে বলিলেনঃ ‘সেই মহান সত্তার শপথ, যিনি বীজ ও আঁটিকে দীর্ণ করিয়া বৃক্ষ উৎপাদন করেন এবং যিনি দেহের ভিতরে প্রানের সঞ্চার করেন, আমার নিকট কুরআন ছাড়া অন্য কোন জিনিসই নাই। তবে কুরআনের সমঝ-বুঝের শক্তি-সামর্থ্য ও যোগ্যতা-প্রতিভা আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা দিয়া থাকেন। ইহা ছাড়া কয়েকটি হাদীস আমার নিকট রহিয়াছে’। (বুখারী, মুসনাদে আহমাদ)
হযরত আলী (রা) তাঁহার কথার শুরুতে যে শপথ করিয়াছেন, উহা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। তাঁহার এই কথা হইতে বুঝা গেল, কুরআনের আয়াতসমূহ আঁটি ও দেহের মত। আর উহার অর্থ, তাৎপর্য ও তত্ত্ব বৃক্ষের মত- যাহা সেই আঁটি ও বীজ হইতে নির্গত হয়। আর উহা সেই প্রাণের মত, যাহা দেহে প্রচ্ছন্ন হইয়া থাকে। অর্থাৎ একটা ক্ষুদ্রাকার বীজ ও আঁটি হইতে যেমন শাখা-প্রশাখা সমন্বিত একটি বিরাট বৃক্ষের উদগম হইতে পারে-যাহা মূলতঃসেই বীজ ও আঁটির মধ্যেই লুক্কায়িত ছিল; আর প্রানশক্তি হইতে-যাহা দেহে প্রচ্ছন্ন হইয়া থাকে-যেমন সমস্ত মানবীয় কর্ম ও কীর্তিকলাপ প্রকাশিত হয়, কুরআনের শব্দসমূহ হইতেও-যাহা দেহের মতই-বিপুল অর্থ ও তাৎপর্য বাহির হইতে পারে।
বস্ততঃ হযরত আলী (রা) যে কুরআনের তত্ত্ব ও দর্শনে বিশেষ বুৎপত্তির অধিকারী ছিলেন, ইহা তাঁহার উক্ত কথাটি হইতেই প্রমাণিত হয়।
হাদীসের ক্ষেত্রেও হযরত আলী (রা)র মনীষা ও বৈদগ্ধ্য ছিল অসাধারণ, বিশাল ও গভীর মহাসমুদ্র সমতুল্য। বাল্যকাল হইতে পূর্ণ ত্রিশটি বৎসর তিনি নবী করীম (স)-এর সাহচর্যে ও নিবিড় সান্নিধ্যে কাটাইয়াছেন। এই কারণে ইসলামের পূর্ণ আইন-বিধান ও রাসূলের বাণী সম্পর্কে হযরত আবূ বকর (রা)-এর পর তিনিই ছিলেন শ্রেষ্ঠ বিশারদ। ইহাছাড়া নবী করীম (স)-এর ইন্তেকালের পর সমস্ত বড় বড় সাহাবীদের মধ্যে তিনিই সর্বাধিক বয়স পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। রাসূলে করীম (স)-এর পর প্রায় ত্রিশটি বৎসর পর্যন্ত তিনি কুরআন, হাদীস এবং দ্বীন ও শরীয়াত প্রচারে নিরন্তর ব্যতিব্যস্ত ছিলেন। প্রথম তিনজন খলীফার আমলেও এই দায়িত্ব তাঁহার উপর ন্যস্ত ছিল। তাঁহার নিজের খিলাফত আমলেও নানা ফিতনা-ফাসাদ ও রক্তাক্ত যুদ্ধ-বিগ্রহ সত্ত্বেও জ্ঞান বিস্তারের এই স্রোত কখনো বন্ধ হয় নাই; বরং ইহা অব্যাহত ধারায় প্রবাহমান ছিল। এই কারণে প্রথম তিনজন খলীফার তুলনায় হাদীস বর্ণনায় অধিক সুযোগ তিনিই লাভ করিয়াছেন। কিন্তু এইসব সত্ত্বেও হাদীস বর্ণনায় তিনি অত্যন্ত বেশী সতর্ক ও কঠোর প্রকৃতির ছিলেন। এই কারণে তাঁহার বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা খুব বেশী হয় নাই। মাত্র ৫৮৬টি হাদীস তাঁহার সূত্রে গ্রন্থাবলীতে উদ্ধৃত হইয়াছে। নবুয়্যাতের জমানায় যে কয়জন সাহাবী হাদীস লিখিয়া রাখিতে অভ্যস্ত ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে হযরত আলী (রা)ও একজন। তাঁহার লিখিয়া রাখা হাদীস সম্পদকে তিনি “সহীফা” নামে উল্লেখিত করিতেন এবং এই ‘সহীফা’ তাঁহার তরবারির খাপের মধ্যে ঢুকাইয়া রাখিতেন। এই হাদীসসমূহ হইতে ব্যবহারিক জীবনের বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের মসআলা জানা যায়।
ফিকাহ ও ইজতিহাদের ক্ষেত্রে তাঁহার যোগ্যতা ও প্রতিভা সর্বজনস্বীকৃত। বড় বড় সাহাবীগণ- এমন কি তাঁহার বিরুদ্ধবাদীরাও-বিভিন্ন বিষয়ে তাঁহার নিকট হইতে শরীয়াতের সিদ্ধান্ত জানিয়া লইবার প্রয়োজনবোধ করিতেন। এই ক্ষেত্রে তাঁহার বিশেষ বুৎপত্তির বড় কারণ এই ছিল যে, তিনি নিজে অনেক বিষয়ে রাসূলে করীম (রা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়া লইতেন।
বিচারপতি হিসাবে হযরত আলী (রা)
হযরত আলী (রা) জীবনের বেশীর ভাগ সময় মদীনায় অতিবাহিত করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার খিলাফতের পুরা সময়টি তিনি কুফায় অবস্থান করিয়াছেন। এই কারণে তাঁহার ফিকাহ সংক্রান্ত মত ও ইজতিহাদ ইরাকেই বেশী প্রচার লাভ করিয়াছে। হানাফী মযহাবের ভিত্তি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের (রা) পরে হযরত আলী (রা)-র মত ও তাঁহার গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের উপরই সংস্থাপিত হইয়াছে। হযরত আলী (রা)-র এই যোগ্যতার কারণে শরিয়াত অনুযায়ী মামলা-মুকাদ্দমার বিচার করার ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে তাঁহার দক্ষতাও সর্বজন স্বীকৃত ছিল। হযরত উমর ফারুক (রা) বলিয়াছেনঃ
********(আরবী)
আমাদের মধ্যে বিচারক হিসাবে অধিক যোগ্য ব্যক্তি হযরত আলী এবং অধিক কুরআন-বিশারদ হযরত উবাই ইবনে কায়াব।
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ(রা) বলিয়াছেনঃ ‘আমরা পরস্পরে বলিতাম যে, মদিনায় সর্বাধিক বিচার-ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি হইতেছেন হযরত আলী (রা)।
স্বয়ং নবী করীম (স)-ও অনেক সময় বিচারকার্যের দায়িত্ব হযরত আলী (রা)র উপর অর্পণ করিতেন। নবী করীম (স) তাঁহাকে ইয়েমেনের বিচারপতির দায়িত্বে নিযুক্ত করিলে তিনি নিজের অযোগ্যতা ও অক্ষমতার কথা বলিয়া সেই দায়িত্ব গ্রহণ হইতে নিষ্কৃতি পাইতে চাহিয়াছিলেন। তখন নবী করীম (স) বলিলেনঃ
আল্লাহ্ তা’আলাই তোমার মুখকে সঠিক পথে এবং তোমার দিলকে দৃঢ় ও ধৈর্যসম্পন্ন করিয়া রাখিবেন।
হযরত আলী (রা) নিজেও বলিয়াছেনঃ
অতঃপর বিচার কার্যে আমি কখনও কোনোরূপ সংশয় বা কুণ্ঠাগ্রস্ত হই নাই।
বিচারকার্য পরিচালনা সম্পর্কে নবী করীম (স) তাঁহাকে বহু মূলনীতি ও নিয়ম-পদ্ধতি শিক্ষা দিয়াছিলেন। একবার তাঁহাকে বলিয়াছিলেনঃ
হে আলী! তুমি যখন দুই ব্যক্তির বিবাদ মীমাংসা করিতে বসিবে, তখন কেবল একজনের কথা শুনিয়াই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে না এবং দ্বিতীয় জনের বক্তব্য না শুনা পর্যন্ত তোমার সিদ্ধান্ত গ্রহণ স্থগিত রাখিবে।
মামলা বিচারের ক্ষেত্রে সন্দেহমুক্ত দৃঢ় প্রত্যয় লাভের জন্য মামলার দুইপক্ষ এবং সাক্ষীদের জেরা করা ও এই ব্যাপারে তাহাদিগকে প্রশ্ন না করা হযরত আলী (রা)-এর সুবিচার নীতির অপরিহার্য অংশরূপে নির্দিষ্ট। অপরাধ স্বীকারকারী(confessor)বার বার প্রশ্ন ও জেরা করার পরও নিজের স্বীকৃতির উপর অবিচল না থাকিলে তিনি এই স্বীকৃতির ভিত্তিতে তাহাকে কোন শাস্তি দিতেন না। সাক্ষীদিগকে নানাভাবে ভীত-সন্ত্রস্ত করার পর সাক্ষ্য-উক্তিতে তাহাদের অবিচল না পাইলে সে সাক্ষ্যের ভিত্তিতে তিনি কোন ফয়সালা করিতেন না। হত্যাসংক্রান্ত মামলার বিচারে তিনি দুর্ঘটনা ও হত্যার ইচ্ছা(Motive)-র মধ্যে পার্থক্য করিতেন। ১ {১.নায়বিচার প্রতিষ্ঠায় সচেতনতাঃ সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠাকে নিশ্চিন্ত করার লক্ষ্যে হযরত আলী (রা) সর্বদা সচেতন থাকিতেন। বিচার ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করার জন্য রাষ্ট্র-ক্ষমতার অপব্যবহারকে তিনি জঘন্য অপরাধ বলিয়া মনে করিতেন। ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তিনি মুসলিম ও অমুসলিম মধ্যেও কোনোরূপ ভেদনীতিকে প্রশ্রয় দিতেন না। এই ব্যাপারে একটি ঐতিহাসিক ঘটনা এখানে উল্লেখযোগ্য। একদা জনৈক ইয়াহুদী আমীরুল মুমিনীন হযরত আলী (রা)র লৌহবর্মটি চুরি করিয়া লইয়া গেল। দেশের সর্বোচ্চ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকা সত্ত্বেও ইনি সরাসরি এ ব্যাপারটি কোন পুলিশী ব্যবস্থা গ্রহণ করিলেন না; বরং প্রচলিত নিয়মনুযায়ী আদালতে গিয়া অভিযোগ দায়ের করিলেন। আদালতের বিচারক তাঁহাকে অভিযোগের সপক্ষে দুইজন সাক্ষী হাজির করার আদেশ দিলেন। হযরত আলী (রা) তাঁহার দুই পুত্র ইমাম হাসান ও ইমাম হুসাইন(রা)-কে সাক্ষী হিসাবে উপস্থিত করিলেন। কিন্তু বিচারক অভিযোগকারীর নিকটাত্মীয় বলিয়া ইহাদের সাক্ষ্য গ্রহণ না করিয়া বরং মামলাটিই খারিজ করিয়া দিলেন। এই ঘটনায় অভিভুক্ত হইয়া অভিযুক্ত ইয়াহুদী নিজেই তাহার অপরাধ স্বীকার করিল এবং পবিত্র কালিমা পড়িয়া ইসলামের কাফেলায় শরীক হইল।–সম্পাদক}
হযরত আলী (রা)-র বিচার-ফয়সালা আইনের দৃষ্টান্তরূপে গণ্য। এই কারণে মনিষীগণ উহা লিপিবদ্ধ করিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু উত্তরকালে দুষ্ট লোকেরা উহাতে নানারুপ বিকৃতির অনুপ্রবেশ ঘটায়। ইহার ফলে আইন বা বিচার জগতে উহা সম্পূর্ণ অকেজো হইয়া যায়।
ব্যাক্তিগত জীবনের কৃচ্ছ্র সাধনা
হযরত আলী (রা) ব্যক্তিগত জীবন অত্যন্ত কঠোর কৃচ্ছ্র সাধনার ভিতর দিয়া অতিবাহিত করিয়াছেন। দারিদ্রের নির্মম কষাঘাতে জর্জরিত হওয়া সত্ত্বেও তিনি মুহূর্তের তরেও বিচলিত হইয়া পড়েন নাই। সময় ও সুযোগ মত শ্রম ও দিন-মজুরী করিয়া জীবিকা সংগ্রহ করিতে তিনি বিন্দুমাত্র সংকোচ বোধ করিতেন না। খলীফার মসনদে আসীন হওয়ার পরও তাঁহার এই কৃচ্ছ্র সাধনায় সামান্য পার্থক্যও সূচিত হইতে পারে নাই। তাঁহার তুচ্ছাতিতুচ্ছ খাবার দেখিয়া লোকেরা স্তম্ভিত ও হতবাক হইয়া যাইত। লোকদের তিনি বলিতেনঃ ‘মুসলমানদের খলীফা রাষ্ট্রীয় বায়তুলমাল হইতে মাত্র দুইটি পাত্র পাইবার অধিকারী। একটিতে নিজে ও নিজের পরিবারবর্গ মিলিয়া খাইবে। আর অপরটি জনগণের সামনে পেশ করিবে’।
তাঁহার ঘরের কাজ সম্পন্ন করার জন্য বাড়তি কোন লোক ছিল না। নবী সম্রাট-তনয়া স্বহস্তেই সমস্ত কাজ সম্পন্ন করিতেন। বৈষয়িক ধন-সম্পদের দিক দিয়া হযরত আলী (রা) শূন্যপাত্র ছিলেন। কিন্তু আত্তার দিক দিয়া তিনি ছিলেন বিপুল সম্পদের অধিকারী। কোন প্রার্থী তাঁহার দুয়ার হইতে খালি হাতে ফিরিয়া যাইতে পারিত না। এমন কি নিজেদের জন্য তৈয়ার করা খাদ্যও তিনি অবলীলাক্রমে ক্ষুধার্ত ভিখারীর হাতে তুলিয়া দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করিতেন না।
--- সমাপ্ত ---
সুচীপত্রঃ
পূর্বকথা
শুরু কথা
ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা
রাষ্ট্রের প্রথম ভিত্তিস্থাপন
মদিনায় ইসলামী রাষ্ট্র
মদীনা-চুক্তির উল্লেখযোগ্য ধারাসমূহ
চূড়ান্ত পদক্ষেপ
নবী-প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য
খিলাফতে রাশেদা
খিলাফত
খিলাফতের মৌল আদর্শ
খুলাফায়ে রাশেদুন
খুলাফায়ে রাশেদুনের নির্বাচন
খিলাফতে রাশেদার বৈশিষ্ট্য
খিলাফতে রাশেদার রাশেদার রাষ্ট্র-রূপ
পরবর্তী খলীফাদের উপাধি
সমসাময়িক আরবের রাজনৈতিক ব্যবস্থা
খিলাফতের রাষ্ট্র-রূপ
আরবের রাজনৈতিক একত্ব
ইসলামী রাষ্ট্র-নীতির অন্তর্নিহিত শক্তি
খিলাফতে রাশেদার আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা
বিচার বিভাগ
দেশরক্ষা বিভাগ
রাজস্ব বিভাগ
খারাজ
উশর
জিযিয়া
যাকাত
শুল্ক
মুদ্রা
হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)
হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর বৈশিষ্ট্য
পবিত্র স্বভাব-প্রকৃতি
নৈতিক বল ও অসমসাহস
মজলুমকে সাহায্য ও সমর্থন দান
হযরতের জন্য আত্মোৎসর্গ
কঠোরতা ও কোমলতার অপূর্ব সমন্বয়
দূরদৃষ্টি ও বিচক্ষণতা
আল্লাহ্, রাসূল ও মুসলিমদের নিকট সমান প্রিয়পাত্র
চরিত্র বৈশিষ্ট্য
দৃঢ়তা ও স্থিরতা
রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি ও প্রজ্ঞা
বিশ্বনবীর স্থলাভিষিক্ত হওয়ার যোগ্যতা
হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর খিলাফত
খিলাফতের পরামর্শ-ভিত্তিক চরিত্র
আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা ব্যবস্থা
শাসকদের প্রতি কড়া দৃষ্টি
দণ্ড বিধানে নম্রতা
খিলাফতের অর্থ বিভাগ
সামরিক ব্যবস্থা
সৈনিকদের চরিত্রগঠন ও প্রশিক্ষন ব্যবস্থা
যুদ্ধের সরঞ্জাম সংগ্রহ
সামরিক কেন্দ্রসমূহ পর্যবেক্ষণ
অনৈসলামী প্রথার প্রতিরোধ
কুরআন ও হাদীস সম্পর্কে হযরত আবূ বকর (রা)-এর ভূমিকা
ইসলামী আইন বিভাগ স্থাপন
ইসলাম প্রচার
নবী করীম (স)-এর ওয়াদাসমূহ পরিপূরণ
নবী করীম (স)-এর পরিবারবর্গ ও আত্মীয়দের সহিত ব্যবহার
যিম্মি প্রজাদের অধিকার রক্ষা
উমর ফারুক (রা)-এর চরিত্র বৈশিষ্ট্য
ফারুকী চরিত্রের মৌল ভিত্তি
রাসূলের প্রতি ভালবাসা ও আনুগত্য
দায়িত্বের তীব্র অনুভূতি
ভোগ-বিলাসে অনীহা ও অল্পোতুষ্টি
হযরত উমর ফারুক (রা)-এর খিলাফত
খিলাফতের রাষ্ট্র-রূপ
ফারুকী খিলাফতের কাঠামো
ফারুকী খিলাফতের আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা
জনগণের নৈতিক মান সংরক্ষণ
আভ্যন্তরীণ শাসন-শৃঙ্খলা ব্যবস্থা
বায়তুলমাল প্রতিষ্ঠা
গৃহ নির্মাণ ও পূর্তবিভাগীয় কাজ
শহর নির্মাণ
সামরিক ব্যবস্থাপনা
ইসলামের প্রচারের কাজ
সাধারণ জনকল্যাণমূলক কাজ
বিচার ইনসাফ
হযরত উসমান (রা)- এর চরিত্র বৈশিষ্ট্য
হযরত উসমান (রা)-এর খিলাফত
ইসলাম গ্রহন
হিজরাত
খলীফারূপে নির্বাচন
খিলাফতের দায়িত্ব পালন
খিলাফতে শাসন পদ্ধতি
দ্বীন-প্রচারের কাজ
হযরত আলী (রা)-এর জীবন ও চরিত্র বৈশিষ্ট্য
প্রাথমিক জীবন
ইসলাম গ্রহণ
দ্বীন প্রচারে সহযোগিতা
মদীনায় কর্মময় জীবন
হযরত আলী (রা)-র খিলাফত
খলীফা নির্বাচন
খলিফারুপে হযরত আলী (রা)
হযরত আলী (রা)র মনীষা
বিচারপতি হিসাবে হযরত আলী (রা)
ব্যাক্তিগত জীবনের কৃচ্ছ্র সাধনা
পূর্বকথা
শুরু কথা
ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা
রাষ্ট্রের প্রথম ভিত্তিস্থাপন
মদিনায় ইসলামী রাষ্ট্র
মদীনা-চুক্তির উল্লেখযোগ্য ধারাসমূহ
চূড়ান্ত পদক্ষেপ
নবী-প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য
খিলাফতে রাশেদা
খিলাফত
খিলাফতের মৌল আদর্শ
খুলাফায়ে রাশেদুন
খুলাফায়ে রাশেদুনের নির্বাচন
খিলাফতে রাশেদার বৈশিষ্ট্য
খিলাফতে রাশেদার রাশেদার রাষ্ট্র-রূপ
পরবর্তী খলীফাদের উপাধি
সমসাময়িক আরবের রাজনৈতিক ব্যবস্থা
খিলাফতের রাষ্ট্র-রূপ
আরবের রাজনৈতিক একত্ব
ইসলামী রাষ্ট্র-নীতির অন্তর্নিহিত শক্তি
খিলাফতে রাশেদার আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা
বিচার বিভাগ
দেশরক্ষা বিভাগ
রাজস্ব বিভাগ
খারাজ
উশর
জিযিয়া
যাকাত
শুল্ক
মুদ্রা
হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)
হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর বৈশিষ্ট্য
পবিত্র স্বভাব-প্রকৃতি
নৈতিক বল ও অসমসাহস
মজলুমকে সাহায্য ও সমর্থন দান
হযরতের জন্য আত্মোৎসর্গ
কঠোরতা ও কোমলতার অপূর্ব সমন্বয়
দূরদৃষ্টি ও বিচক্ষণতা
আল্লাহ্, রাসূল ও মুসলিমদের নিকট সমান প্রিয়পাত্র
চরিত্র বৈশিষ্ট্য
দৃঢ়তা ও স্থিরতা
রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি ও প্রজ্ঞা
বিশ্বনবীর স্থলাভিষিক্ত হওয়ার যোগ্যতা
হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর খিলাফত
খিলাফতের পরামর্শ-ভিত্তিক চরিত্র
আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা ব্যবস্থা
শাসকদের প্রতি কড়া দৃষ্টি
দণ্ড বিধানে নম্রতা
খিলাফতের অর্থ বিভাগ
সামরিক ব্যবস্থা
সৈনিকদের চরিত্রগঠন ও প্রশিক্ষন ব্যবস্থা
যুদ্ধের সরঞ্জাম সংগ্রহ
সামরিক কেন্দ্রসমূহ পর্যবেক্ষণ
অনৈসলামী প্রথার প্রতিরোধ
কুরআন ও হাদীস সম্পর্কে হযরত আবূ বকর (রা)-এর ভূমিকা
ইসলামী আইন বিভাগ স্থাপন
ইসলাম প্রচার
নবী করীম (স)-এর ওয়াদাসমূহ পরিপূরণ
নবী করীম (স)-এর পরিবারবর্গ ও আত্মীয়দের সহিত ব্যবহার
যিম্মি প্রজাদের অধিকার রক্ষা
উমর ফারুক (রা)-এর চরিত্র বৈশিষ্ট্য
ফারুকী চরিত্রের মৌল ভিত্তি
রাসূলের প্রতি ভালবাসা ও আনুগত্য
দায়িত্বের তীব্র অনুভূতি
ভোগ-বিলাসে অনীহা ও অল্পোতুষ্টি
হযরত উমর ফারুক (রা)-এর খিলাফত
খিলাফতের রাষ্ট্র-রূপ
ফারুকী খিলাফতের কাঠামো
ফারুকী খিলাফতের আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা
জনগণের নৈতিক মান সংরক্ষণ
আভ্যন্তরীণ শাসন-শৃঙ্খলা ব্যবস্থা
বায়তুলমাল প্রতিষ্ঠা
গৃহ নির্মাণ ও পূর্তবিভাগীয় কাজ
শহর নির্মাণ
সামরিক ব্যবস্থাপনা
ইসলামের প্রচারের কাজ
সাধারণ জনকল্যাণমূলক কাজ
বিচার ইনসাফ
হযরত উসমান (রা)- এর চরিত্র বৈশিষ্ট্য
হযরত উসমান (রা)-এর খিলাফত
ইসলাম গ্রহন
হিজরাত
খলীফারূপে নির্বাচন
খিলাফতের দায়িত্ব পালন
খিলাফতে শাসন পদ্ধতি
দ্বীন-প্রচারের কাজ
হযরত আলী (রা)-এর জীবন ও চরিত্র বৈশিষ্ট্য
প্রাথমিক জীবন
ইসলাম গ্রহণ
দ্বীন প্রচারে সহযোগিতা
মদীনায় কর্মময় জীবন
হযরত আলী (রা)-র খিলাফত
খলীফা নির্বাচন
খলিফারুপে হযরত আলী (রা)
হযরত আলী (রা)র মনীষা
বিচারপতি হিসাবে হযরত আলী (রা)
ব্যাক্তিগত জীবনের কৃচ্ছ্র সাধনা

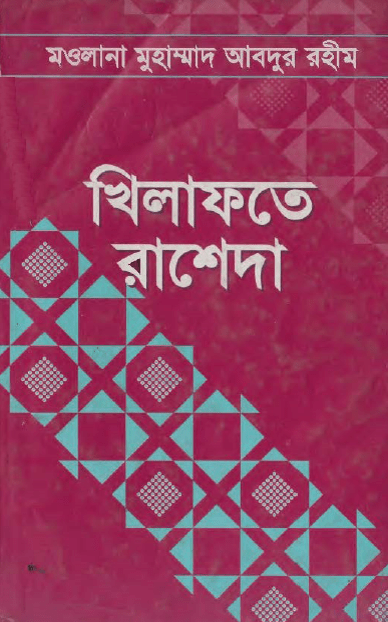 স্ক্যান কপি ডাউনলোড
স্ক্যান কপি ডাউনলোড