লেখকের কৈফিয়ত
১৪০১ হিজরীর রমজান ও শাওয়াল মাসে (১৯৮১ খৃঃ) মুসলিম তরুণদের পুনর্জাগরণ সম্পর্কিত আমার দু’টি প্রবন্ধ ‘আল-উম্মাহ’ ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়। আমি এই জাগরণের ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় দিকের ওপর আলোকপাত করি। এটি এখন ব্যাপকভাবে মুসলিম পর্যবেক্ষক, ধর্মপ্রচারক, সুধীজনের বিবেচ্য বিষয়। আমি ঐ প্রবন্ধে মুসলিম তরুণদের পুনর্জাগরণের জোয়ারকে সঠিক খাতে প্রবাহিত করার লক্ষ্যে তাদের সাথে পিতৃসুলভ মনোভাব নিয়ে আলাপ-আলোচনা পরামর্শ দিয়েছিলাম। আমার মতামত মুসলিম বিশ্বে এমন ব্যাপক সাড়া জাগাতে সক্ষম হয় যে, আমার লেখাগুলো কয়েকটি ভাষায় অনুদিত হয়। অনেক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা আমার প্রবন্ধগুলো গুরুত্বের সাথে পাঠ করে, যদিও এতে আমি তাদের অনেকেরই সমালোচনা করেছি।
আমি আনন্দের সাথে এখানে উল্লেখ করছি যে, কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ইসলামী সংস্থা ১৯৮১ সালে তাদের গ্রীষ্মকালীন শিবিরে আমার মতামতগুলো নিয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা করে। তারা ঐ লেখাগুলো ছাপিয়ে প্রকাশ করে এবং আগ্রহী ব্যক্তিদের মধ্যে বিতরণ করে। এতে তাদের প্রশংসনীয় সচেতনার পরিচয় পাওয়া যায়; সেই সাথে মধ্যপন্থার প্রতি তাদের সমর্থনসূচক মনোভাবের প্রতিফলন স্পষ্ট হয়ে ওঠে।
আমি এখানে সাম্প্রতিক মুসলিম তরুণ ও ক্ষমাতাসীনদের মধ্যে সংঘাত সৃষ্টিকারী ঘটনা প্রবাহের ওপর আলোচনায় লিপ্ত হতে চাই না। এই আশঙ্কায় নয় যে, আমার আলোচনা উত্তেজনা প্রসারের কারণ হবে, বরং ‘আল-উম্মাহ’ ম্যাগাজিনের অবস্থানগত দিক বিবেচনা করেই আমাকে এই নীতি অবলম্বন করতে হয়েছে। কারণ, এই পত্রিকাটি বিশেষ একটি গ্রুপের নয়, বরং সমগ্র উম্মাহর স্বার্থ সমুন্নত করার মহান দায়িত্বে নিয়োজিত। আমি এখানে মূলত ধর্মীয় চরমপন্থা বা গোঁড়ামীর বিষয় নিয়ে আলোচনার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছি। কারণ এ থেকে উদ্ভুত ঘটনাবলী দীর্ঘ ও উত্তপ্ত আলোচনার কেন্দ্র বিন্দুতে পরিণত হয়েছে। আর এহেন বাক-বিতন্ডায় স্রেফ জ্ঞানী-গুনীরাই জড়িয়ে পড়ছেন না, ইসলাম সম্পর্কে এমন অজ্ঞ ব্যক্তিরাও এতে সোৎসাহে শামিল হচ্ছেন ইসলামের প্রতি যাদের শত্রুতা, অবহেলা ও বিদ্রুপ সুবিদিত। কয়েক বছর আগে আল-আরাবী পত্রিকার পক্ষ থেকেও “ধর্মীয় চরমপন্থা” স্বরুপ ও বৈশিষ্ট্য উদ্ঘাটন করে আমাকে লেখার অনুরোধ জানানো হয়েছিল। ১৯৮২ সালের জানুয়ারী মাসে প্রবন্ধটি প্রকাশিত হলে আমার কতিপয় বন্ধু আমাকে এই বলে দোষারোপ করলেন যে, আমি নাকি এমন এক বিষয়ে কলম ধরেছি যেখানে বাতিলের পক্ষে হককে বিকৃত করা হচ্ছে। অবশ্য আমার বন্ধুরা আমার প্রবন্ধের মর্ম বা বক্তব্য বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন না তুললেও, সম্প্রতি ধর্মীয় চরমপন্থার বিরুদ্ধে যে প্রচারাভিযান চালানো হচ্ছে তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে তারা সংশয়ের আবর্তে দোল খাচ্ছেন। এই অভিযান আসলেই চরমপন্থাকে প্রতিহত করতে অথবা চরমপন্থীদের মধ্যপন্থার দিকে পরিচালিত করতে চায় কিনা সে ব্যাপারে তারা স্থির নিশ্চিত নন। তাদের আশংকা ইসলামী পুনর্জাগরণ একটি তাৎপর্যপূর্ণ রাজনৈতিক শক্তিতে রুপান্তরিত হওয়ার পূর্বে একে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করার জন্যে এসব প্রচারাভিযান শুরু করা হয়েছে। বন্ধুরা বলছেন, বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ন ইস্যুতে সরকারের বিরোধিতায় লিপ্ত হলেই সরকার ধর্মনিষ্ঠ তরুনদের প্রতি দৃষ্টি দিতে শুরু করেন। এর একটি প্রমাণ এই যে, ক্ষমতাসীন শাসকগোষ্ঠী আসলে গোঁড়া ধর্মীয় গ্রুপগুলোকে পৃষ্ঠপোষকতা দান করেন, উদ্দেশ্য অন্যান্য ইসলামী আন্দোলনের বিরুদ্ধে এদেরকে ব্যবহার করা। অত:পর তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়ে গেলে তারা ঐ ধর্মীয় গ্রুপগুলোকে উৎখাত করেন। এই হিসেবে বন্ধুদের যুক্তি হচ্ছে, কর্তৃপক্ষের ও ধর্মীয় গ্রুপগুলোর মধ্যেকার সংঘর্ষের কারণগুলো ধর্মীয় চরমপন্থা বা গোঁড়ামীর ভিত্তি হিসেবে খাড়া করা যায় না। তারা আরো মনে করেন যে, মুসলিম দেশগুলোর শাসকরা ইসলামী আন্দোলনকেই সবচেয়ে মারত্মক শত্রু হিসেবে গণ্য করেন। এরূপ কর্তৃপক্ষ চরম ডান অথবা চরম বামের সাথে আঁতাত গড়তে পারে, কিন্তু ইসলামী আন্দোলনের সাথে কখনো নয়।
কখনো কখনো তারা এই আন্দোলনের সাথে সংঘর্ষে অস্থায়ীভাবে বিরতি দেন আবার কখনো কখনো তাদের রাজনৈতিক ও আদর্শিক প্রতিপক্ষের সাথে সংঘাতের মধ্যে ইসলামী আন্দোলনকেও জড়িয়ে ফেলার অপচেষ্টা চালান। পরিশেষে কর্তৃপক্ষ ও প্রতিপক্ষ দেখতে পান যে, তাদের উদ্দেশ্য ও উপায়ের মধ্যে সাদৃশ্য আছে। অতএব ইসলামী আন্দোলনের বিরুদ্ধে তাদের আঁতাত গড়তে বিন্দুমাত্র বিলম্ব হয় না। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কুরআনুল কারীমে ঘোষণা করেছেন, “আল্লাহর মুকাবিলায় তারা তোমার কোন উপকার করতে পারবে না; যালিমরা একে অপরের বন্ধু; আর আল্লাহ্ তো মুত্তাকীদের বন্ধু।”(৪৫:১৯) বর্তমান ঘটনাবলীই এর সত্যতা বহন করে। মিসরে ইসলামী গ্রুপগুলোকে চরমপন্থী রূপ নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিল। কিন্তু ক্রমান্বয়ে তারা নরম ও মধ্যপন্থী দৃষ্টি গ্রহণ করতে শুরু করে। এর কৃতিত্ব অবশ্য বিভিন্ন মুসলিম চিন্তাবিদ ও ধর্মপ্রচারকদের প্রাপ্য। তারা ঐ গ্রুপগুলোকে ওপর তাদের চিন্তার প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হন। ফলত এখন অধিকাংশ ইসলামী গ্রুপের মধ্যে নরম ও মধ্যপন্থার লক্ষণগুলো স্পষ্ট হয়ে ওঠেছে। বিম্ময়ের ব্যাপার, চরমপন্থার প্রাধান্যের সময় ক্ষমতাসীনরা চুপচাপ ছিলেন; কিন্তু মধ্যপন্থী প্রবণতা জোরদার হওয়ার সাথে সাথে তারা ঐ গ্রুপগুলোকে নিশ্চিহ্ন করার জন্যে সর্বশক্তি নিয়োগ করেন।
এই হতাশাব্যঞ্জক পরিস্থিতি সম্পর্কে আমি যে অসতর্ক ছিলাম তা নয়, বরং এসব অবস্থা সামনে রেখেই ‘আল-আরাবী\'তে প্রকাশিত আমার প্রবন্ধের গোড়াতেই আমি লিখেছিলাম:
‘আল-আরাবী’ যে মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে ‘ধর্মীয় চরমপন্থার’ মত বিষয়ে আলোচনার আহবান জানিয়েছে তার গুরুত্ব আমি দ্বিধাহীন চিত্তে স্বীকার করি। এসত্ত্বেও সমসাময়িক ঘটনাবলীতে এর প্রতিক্রিয়ার কথা চিন্তা করে প্রথমে আমি বিষয়টি নিয়ে লেখার ব্যাপারে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলাম। বিশেষ করে আমার এই আশংকা ছিল যে, আমি যা কিছু লিখব তার অপব্যাখ্যা হতে পারে অথবা আমার কিংবা পত্রিকাটির ইচ্ছার বিপরীতে অন্য কোন উদ্দেশ্যে এর অপপ্রয়োগ হতে পারে।
বস্তুত বর্তমানে লেখক ও বক্তারা ধর্মীয় চরমপন্থাকে তাদের আক্রমণের লক্ষ্য বস্তুতে পরিণত করেছে। আমি দুর্বলের বিরুদ্ধে সবলের পক্ষ নিতে চাই না। আর এটাও সত্য যে, বিরোধী বা প্রতিপক্ষের তুলনায় ক্ষমতাসীন কর্তৃপক্ষ শক্তিশালী অবস্থানে থাকেন। বলাবাহুল্য, ইসলামপন্থীরা আত্মপক্ষ সমর্থনেরও অধিকার পান না। সংবাদ মাধ্যমে মত প্রকাশের স্বাধীনতা তো নেই-ই, এমনকি মসজিদের প্লাটফরমকেও এ উদ্দেশ্যে ব্যবহারের সুযোগ নেই।
আমার দ্বিধাদ্বন্দ্ব আরেকটি কারণে জোরদার হয়েছে যে, গত কয়েক দশক ধরে ইসলাম বিরোধীরা ইসলামপন্থীদের বিরুদ্ধে রাশি রাশি অভিযোগ উত্থাপন করে চলেছে। তাদেরকে প্রতিক্রিয়াশীল, গোঁড়া, শত্রু, বিদেশের দালাল ইত্যাদি অভিযোগে ‘ভূষিত’ করা হয়। অথচ কোন পর্যবেক্ষকেরই এটা বুঝতে বাকী থাকে না যে, পূর্ব ও পশ্চিমের উভয় পরাশক্তি বলয় ইসলামপন্থীদের প্রতি বৈরী মনোভাব পোষণ করে এবং তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করার সকল সুযোগের অপেক্ষায় থাকে।
যা হোক, অনেক চিন্তা-ভাবনার পর আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, বিষয়টি একটি বিশেষ দেশের নয় বরং সারা মুসলিম জাহানের সমস্যা। নীরবতা অবলম্বন করলেই বিষয়টির নিষ্পত্তি হবে না। আলোচনায় শামিল না হওয়াটাই বরঞ্চ জিহাদের ময়দান থেকে পলায়নের মতোই অনৈসলামী কাজ। সুতরাং আমি নিজেকে আল্লাহ কাছে সোপর্দ করে প্রকৃত সত্য প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলি। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) একটি হাদীসে বলেছেন: ‘নিয়তের ওপরই কর্মের ফলাফল নির্ভর করে এবং প্রত্যেক ব্যক্তি সেই ফলই পাবে যার নিয়ত সে করেছে।” (বুখারী ও মুসলিম)
অনেক লেখক অজ্ঞতাবশত অথবা উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে কিংবা বিষয়টির প্রকৃতি সম্পর্কে অগভীর ধারণার দরুন মুক্তকচ্ছের মতো বক্তব্য রেখে গেছেন। এমতাবস্থায় এই অভিযানে অংশ নিয়ে মুসলিম চিন্তাবিদদের সত্য প্রকাশে ব্রতী হওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না।
তাছাড়া ধর্মীয় চরমপন্থা বিষয়টির প্রতি আমার দীর্ঘদিনের আগ্রহ আমার সংকল্পকে আরো জোরদার করেছে। কয়েক বছর আগে আমি তাকফীরের (কাউকে কাফির ঘোষণার প্রবণতা) বাড়াবাড়ি সম্পর্কে ‘আলমুসলিমুল মুয়াসির’ পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লিখেছিলাম। “মুসলিম তরুণদের পুনর্জাগরণ” শীর্ষক আমার আরেকটি প্রবন্ধ ‘আল-উম্মাহ’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। আমি যখনি মুসলিম তরুণদের সাথে মুখোমুখী কিংবা শিবির ও সেমিনারে আলোচনার সুযোগ পেয়েছি তখনি তাদেরকে মধ্যপন্থার প্রতি আহবান জানিয়েছি এবং বাড়াবাড়ির পরিণাম সম্পর্কে হুঁশিয়ার করে দিয়েছি। অবশ্য ‘আল-আরাবী\'তে যে প্রবন্ধটি লিখেছিলাম তা ছিল সুনির্দিষ্ট বিষয়ের ওপর একটি ফরমায়েশী লেখা।
এসব কাণে আমি বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার তাগিদ অনুভব করি। বিশেষত ধর্মীয় চরমপন্থার বাস্তবতা, কারণ ও প্রতিকার প্রসঙ্গে বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা হওয়া দরকার এবং তা হওয়া দরকার ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে। যারা বিষয়টিকে বিকৃত ও অসদুদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে চায় তাদের তৎপরতা সত্ত্বেও আমি এগিয়ে যেতে সংকল্পবদ্ধ। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন: “মধ্যপন্থীরা এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্ম পর্যন্ত জ্ঞানের পতাকা বহন করে নিয়ে যাবে। তারাই জ্ঞানকে বিকৃতি ও অপব্যাখ্যার হাত থেকে রক্ষা করবে।”
হাদীসটি এই ইঙ্গিত দেয় যে, আল্লাহর ক্রোধ থেকে বাঁচার জন্যে বিজ্ঞ ব্যক্তিদেরকে সত্য গোপন নয়, প্রকাশ করার দায়িত্ব পালন করতে হবে। অতএব যারা বিষয়টির সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত তাদেরকেও এ দায়িত্ব পালন করা উচিত। বাড়াবাড়ির জন্যে কেবল তরুণদের দায়ী করা সঙ্গত নয়। যারা ইসলামের শিক্ষা পালনে ঔদাসীন্য প্রদর্শন করেন অথচ নিজেদেরকে নির্দোষও ভাবেন তারাও সমভাবে দায়ী। নামধারী মুসলমানরা- তা পিতামাতা, শিক্ষক-পন্ডিত অথবা যে কেউ হোন- নিজ নিজ দেশেই ইসলাম, ইসলামপন্থী ও ইসলাম প্রচারকদেরকে প্রায় অস্পৃশ্য করে রেখেছেন। এটা আশ্চর্যের ব্যাপার, আমরা চরমপন্থার সমালোচনায় সোচ্চার হয়ে উঠি, কিন্তু আমাদের নিজস্ব গোঁড়ামি অর্থাৎ ধর্মীয় বিধি-বিধান পালনে অবহেলা ও শিথিলতার প্রশ্নে নির্বিকার। আমরা তরুণদেরকে গোঁড়ামি ও বাড়াবাড়ি পরিহার করার উপদেশ দিই এবং তাদেরকে নমনীয় ও সুবিবেচক হতে বলি, কিন্তু প্রবীণদেরকে কখনো বলি না যে, আপনারাও মুনাফেকী, মিথ্যাচার, প্রতারণা তথা সর্বপ্রকার স্ববিরোধিতা থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করুন। আমরা তরুণদের কাছ থেকে সব কিছু দাবী করি, কিন্তু তাদেরকে যা নসিহত করি নিজেরা তা পালন করি না, যেন সব অধিকার আমাদের আর কর্তব্যের দায়ভার সবটাই যেন তরুণদের। অথচ দায়িত্ব ও কর্তব্য সকলের ওপর সমানভাবে প্রযোজ্য। আজ আমাদের যা প্রয়োজন তা হচ্ছে, প্রচন্ড সাহস সঞ্চয় করে আমাদের স্বীকার করতে হবে যে, আমাদের নিজেদের দুষ্কর্মের দরুনই তরুণরা ধর্মীয় চরমপন্থার আশ্রয় নিয়েছে। আমরা কুরআন তিলাওয়াত করি, কিন্তু এর আহকাম মেনে চলি না, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)- এর প্রতি ভালবাসার দাবী করি, কিন্তু কার্যত তাঁর সুন্নাহ পালন করি না। আরো মজার ব্যাপার আমারা ইসলামকে রাষ্ট্র ধর্ম বলে ঘোষণা করি, কিন্তু আইন-কানুন প্রণয়নের সময় ইসলামের নাম গন্ধ খুঁজে পাওয়া যায় না। প্রকৃতপক্ষে আমাদের স্ববিরোধী ও মুনাফেকী আচরণের জন্যেই তরুণরা আমাদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজেরাই ইসলামকে বোঝার চেষ্টা করছে। কেননা, তাদের দৃষ্টিতে পিতামাতাদের অবস্থা হতাশাব্যঞ্জক। আলিমরা উদাসীন, শাসকরা বৈরী আর পরামর্শদাতার ছিদ্রান্বেষী। অতএব তরুণদের প্রতি শান্ত, সংযত ও সুবিবেচক হওয়ার উপদেশ দেয়ার আগে আমাদের নিজেদেরকে ও সমাজকে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী সংস্কার করতে হবে। চরমপন্থা নির্মূল ও তরুণদের মধ্যে ইসলামী পুনর্জাগরণেকে সঠিক খাতে প্রবাহিত করার ব্যাপারে সরকারী ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্তব্য ও ভূমিকার প্রতি কর্তৃপক্ষ ও চিন্তাশীল লেখকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।
অনেকে মনে করেন, সকল প্রকার চরমপন্থা ও বিচ্যুতিসহ যা কিছু ঘটেছে বা ঘটে চলেছে তার জন্যে সরকারী ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোই দায়ী। বস্তুত এই প্রতিষ্ঠানগুলোর গুরুত্ব অনস্বীকার্য হলেও এদের ওপর আরোপিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনে তারা অক্ষম; কেননা ক্ষমতাসীন কর্তৃপক্ষ তাদের নীতির প্রতি প্রশংসা ও সমর্থন আদায়ের মতলবে এসব প্রতিষ্ঠানকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেন। অথচ সকলে একথা স্বীকার করবেন যে, মুসলিম বিশ্বের এই ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো সরকারী হস্তক্ষেপমুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ পেলে তরুণদের পথ নির্দেশ ও জ্ঞান প্রদানের ক্ষেত্রে অবশ্যই ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে পারে। কিন্তু এই স্বাধীনতার অভাবে এগুলো প্রানহীন কংকালে পর্যবসিত হয়েছে।
আবার এটাও আমাদেরকে স্মরন রাখতে হবে যে, উপদেষ্টাদের প্রতি যদি তরুণদের আস্থা না থাকে তবে সেসব উপদেষ্টার উপদেশ অর্থহীন। পারষ্পরিক আস্থা না থাকলে প্রতিটি উপদেশ বাগাড়ম্বরের নামান্তর। প্রকৃতপক্ষে সরকার নিযুক্ত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে শরীয়তের শিক্ষার যে যথার্থ প্রতিফলন ঘটে না তা মনে করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। এগুলো আসলেই সরকারের হাতের ক্রীড়নক মাত্র। তারা যদি সত্যিকার অর্থে সমাজে তাদের প্রভাব রাখতে চায় তবে সর্বপ্রথম তাদের ঘরকেই আগে সাজাতে হবে। এজন্যে তাদেরকে সদা অস্থির রাজনৈতিক কুচক্রের মধ্যে জড়িয়ে পড়া চলবে না। তাদের প্রধান কাজ হবে এমন এক দল ফকীহ গড়ে তোলা যারা হবে ইসলাম সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের অধিকারী ও যুগসচেতন অর্থাৎ কুরআনের ভাষায় “যারা আল্লাহর বাণী পৌঁছিয়ে দেয় এবং তাঁকে ছাড়া আর কাউকে ভয় করে না।” (৩৩ : ৩৯) বস্তুত আমাদের বর্তমান সমাজে এরূপ অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন সৎ মনীষীর প্রয়োজন অনস্বীকার্য। কেবল এরাই ইসলামী পুনর্জাগরণের লক্ষ্যে তরুণ সমাজকে সঠিক পথ নির্দেশ দিতে পারেন। যেসব লোক ইসলামী পুনর্জাগরণ থেকে দূরে সরে আছেন অথবা এর আশা-আকাঙ্খা উপলব্দি না করে এবং হতাশা ও দুর্ভোগের অংশীদার না হয়েই কেবল সমালোচনা করে চলেছেন তারা কখোনোই এই আন্দোলনের ইতিবাচক অবদান রাখতে পারে না। আমাদের একজন প্রাচীন কবি লিখেছেন : “যারা নিঃস্বার্থ যাতনা ভোগ করে তারা ছাড়া আর কেউ তীব্র আকাঙ্খার তীক্ষ্ম বেদনা উপলব্ধি করতে পারে না।” ইসলামের প্রচার ও প্রসারে যাদের হৃদয়ে আকাঙ্খা নেই তারা আসলেই আত্মকেন্দ্রিক আর এসব লোকের কোনো অধিকার নেই ইসলাম অনুরাগীদের ভুল ধরার অথবা তাদের সংশোধনের জন্যে নসিহত করার। যদি তারা গায়ের জোরে এই অধিকার প্রয়োগ করতে চায় তাহলে কেউ তাদের কথায় কর্ণপাত করবে না।
উপসংহারে, আমার পরামর্শ হচ্ছে যারা তরুণদের উপদেশ দিতে আগ্রহী তাদেরকে পাণ্ডিত্যাভিমান পরিহার করে আইভরি টাওয়ার থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। ধুলির ধরণীতে নেমে এসে তরুণদের সাথে মিশতে হবে। যুব সমাজের আশা-আকাঙ্খা, সংকল্প, উদ্দীপনা ও সৎ কর্মগুলোর যথাযথ মূল্যায়ণপূর্বক তাদের ইতিবাচক ও নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য করতে হবে যাতে তাদেরকে সঠিক দিক নির্দেশনা দেয়া যায়।
ড. ইউসুফ আল-কারজাভী
বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম
প্রথম অধ্যায়
অভিযোগ ও বাস্তবতা
কোন বিষয়ে স্বচ্ছ ধারণা না থাকলে সে বিষয়ে মতামত প্রকাশ করা সমীচীন নয়। তাই যুক্তিবাদীরা মনে করেন অজ্ঞাত ও অস্পষ্ট বিষয় মত প্রকাশ করা উচিত নয়।
সুতরাং ধর্মীয় গোঁড়ামী ও চরমপন্থাকে আমাদের উক্ত প্রেক্ষিতেই বিচার করতে হবে। এর ভাল বা মন্দ বিচারের আগে এর প্রকৃত তাৎপর্য জানতে হবে। এজন্যে সর্বাগ্রে প্রয়োজন এর বাস্তবতা ও বৈশিষ্ট্যগুলোর বিশ্লেষণ। আক্ষরিক অর্থে, উগ্রতাবাদ বা চরমপন্থার অর্থ হচ্ছে কেন্দ্র থেকে সম্ভাব্য সর্বশেষ প্রান্তে অবস্থান। বাহ্যত, এটা ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ, চিন্তাধারা তথা আচার-আচরণের ক্ষেত্রে অনুরূপ দূরত্বে অবস্থানের দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করে। চরমপন্থার একটি অন্যতম পরিণাম হচ্ছে এটি সমাজকে বিপজ্জনক ও নিরাপত্তাহীন পরিস্থিতির দিকে ঠেলে দেয়। অথচ ঈমান, ইবাদত, আচার-আচরণ, আইন-বিধি তথা জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইসলাম মধ্যম সুষমপন্থা অবলম্বনের সুপারিশ করেছে। এটাকেই আল্লাহ তায়ালা ‘সিরাতুল মুস্তাকীম’ বা সহজ সরল পথ বলে উল্লেখ করেছেন। এ পথের একটি সুনির্দিষ্ট ও সুষ্পষ্ট বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এর বিপরীত যতো মত পথ রয়েছে তার অনুসারীরা আল্লাহর গযবে পতিত হয়েছে। মোটকথা, আল্লাহ নির্দেশিত সিরাতুল মুস্তাকীমই হচ্ছে সুপথ আর এর উল্টো পথই হচ্ছে কুপথ বা বিপথ। তাই মধ্যম বা ভারসাম্যময় পন্থা ইসলামের কেবল সাধারণ বৈশিষ্ট্য নয় বরং এর মধ্যেই ইসলামের মৌলিক পরিচয় নিহিত। এ প্রসঙ্গে কুরআনের ঘোষণা:
“এমনিভাবে আমরা তোমাদেরকে একটি মধ্যপন্থী উম্মাহ হিসেবে সৃজন করেছি যাতে তোমরা মানব জাতীর জন্যে সাক্ষী হবে আর রাসূল (সা) তোমাদের জন্যে সাক্ষী হবেন।” (২: ১৪৩)
এই দৃষ্টিতে,মুসলিম উম্মাহ একটি সুবিচারপূর্ণ ও ভারসাম্যপূর্ণ পন্থার পথিক। একইভাবে এই জাতি ইহলৌকিক ও পরলৌকিক জীবনে সরল পথ থেকে মানুষের প্রতিটি বিচ্যুতির বিরুদ্ধে সাক্ষী। ইসলামে এমন কিছু পরিভাষা রয়েছে যাতে মধ্যপন্থা অবলম্বনের এবং সব ধরনের চরমপন্থা ও হঠকারিতা প্রত্যাখ্যান ও পরিহারের আহবান জানানো হয়েছে। যেমন গুলু (বাড়াবাড়ি), তানাতু (উদ্রতা) ও তাশদীদ (কঠোরতা) -এই পরিভাষাগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ইসলাম বাড়াবাড়িতে শুধু নিরুৎসাহিত করেনি বরং এর বিরুদ্ধে কঠোর হুঁসিয়ারী উচ্চারণ করেছে। নিম্নোক্ত হাদীসগুলোতে এর সত্যতা পাওয়া যায়।
১. “ধর্মে বাড়াবাড়ি সম্পর্কে সাবধান! তোমাদের পূর্ববর্তী (জাতিগোষ্ঠি) এরূপ বাড়াবাড়ির পরিণামে নিশ্চিহ্ন হয়েছে।” (আহমাদ, নাসাই ও ইবনে মাজাহ) এখানে জাতি বলতে অন্যান্য ধর্মাবলম্বী জাতিগোষ্ঠিকে বোঝানো হয়েছে।” এর মধ্যে আহলে কিতাব বিশেষত খ্রীষ্টানরা উল্লেখযোগ্য। এদেরকে সম্বোধন করে আল-কুরআন বলছে: “বলুন, হে আহলে কিতাব! তোমরা তোমাদের দ্বীন সম্বন্ধে অন্যায় বাড়াবাড়ি করো না; এবং যে-সম্প্রদায় অতীতে বিপথগামী হয়েছে এবং অনেককে বিপথগামী করেছে এবং সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে তাদের স্বেচ্ছাচারিতার অনুসরণ করো না”। (৫:৭৭)
উপরোক্ত কারণে মুসলমানদেরকে বিপথগামীদের পথ অনুসরণ থেকে বিরত থাকার কঠোর তাগিদ দেয়া হয়েছে। যারা অন্যের ভুলভ্রান্তি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে প্রকৃতপক্ষে তারাই অধিকতর সুখী। তদুপরি বাড়াবাড়ি বা সীমালংঘন (আল-গুলু) এমন অর্থহীন কর্মকান্ডে প্ররোচিত করে যার তান্ডব আমাদের অগোচরে বিস্তৃত হয়ে শেষ পর্যন্ত গোটা সমাজদেহকে একটা হুমকির মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়। হযরত মুহাম্মদ (সা:) বিদায় হজ্জের সময় মুজদালিফায় পৌঁছে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) কে কিছু প্রস্তরখন্ড সংগ্রহ করতে বললেন। ইবনে আব্বাস (রা) কিছু প্রস্তর খন্ড সংগ্রহ করে আনলেন। রাসুলুল্লাহ (সা) পাথরগুলোর আকার দেখে সন্তোষ প্রকাশ করে বললেন: “হ্যাঁ, এই পাথরগুলোর মতোই ধর্মীয় ব্যাপারে বাড়াবাড়ি বা জবরদস্তি থেকে সাবধান।” (ইমামা আহমাদ, আন-নাসাই, ইবনে কাছীর ও হাশীম) এ থেকে এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, মুসলমানরা যেন অতি উৎসাহী হয়ে বড় পাথর ব্যবহারের মতো বাড়াবাড়িতে প্রবৃত্ত না হয়। ইমাম ইবনে তাইমিয়াও ঈমানের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল ক্ষেত্রে তথা ইবাদত ও লেনদেনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ির বিরুদ্ধে সতর্ক করে দিয়েছেন। তিনি খ্রীষ্টানদেরকে বিশ্বাস ও আচরণের ব্যাপারে সবচেয়ে সীমালংঘনকারী জাতি হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ পাকও কুরআনুল কারীমে তাদেরকে ভৎসনা করে বলেছেন, “ধর্মীয় বিষয়ে তোমরা সীমালংঘন করো না” (৪:১৭১)
২. “তারা অভিশপ্ত, যারা চুল ফাঁড়তে (অর্থাৎ ক্ষুদ্র বিষয়ে) লিপ্ত এবং রাসুলূল্লাহ (সা) তিনবার এই কথা উচ্চারণ করলেন।”(মুসলিম, আহমাদ ও আবু দাউদ) ইমাম আননববী বলেন, “এখানে ‘চুল ফাঁড়তে’ লিপ্ত ব্যক্তিদের বলতে তাদের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যারা কথায় ও কাজে সীমা অতিক্রম করে।” উল্লিখিত দু’টি হাদীসে স্পষ্টত এ কথাই ব্যক্ত করা হয়েছে যে, বাড়াবাড়ি ও হঠকারিতার পরিণামে মানুষ সম্পূর্ণরূপে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক ক্ষতির সম্মুখীন হবে।
৩. রাসুলুল্লাহ (সা) বলতেন, “নিজের ওপর এমন অতিরিক্ত বোঝা চাপিও না যাতে তোমার ধ্বংস হওয়ার আশঙ্কা থাকে। তোমাদের পূর্ববর্তী জনগোষ্ঠী নিজেদের ওপর অতিরিক্ত বোঝা চাপিয়ে ধ্বংস হয়েছে। তাদের ধ্বংসাবশেষ পুরাতন মঠ-মন্দিরে খুঁজে পাওয়া যায়।” আবু ইয়ালা তার মসনদে আনাস ইবনে মালিকের বরাতে এবং ইবনে কাছীর সূরা হাদীদের ২৭ আয়াতের তাফসীরে এই হাদীস উল্লেখ করেছেন। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা) সর্বদা ধর্মীয় বাড়াবাড়ির প্রবণতাকে প্রতিহত করতে চেয়েছেন। তিনি তাঁর সাহাবীদের মধ্যে যাদেরকে ইবাদত-বন্দেগীতে বাড়াবাড়ি করতে দেখেছেন, সংসার ধর্ম পালনে বিমুখ দেখেছেন তাদেরকে প্রকাশ্যে ভৎসনা করেছেন। কারণ এসবই হচ্ছে ইসলামের মধ্যপন্থার পরিপন্থী। ইসলাম দেহ ও আত্মার সুষম বিকাশ চায় অর্থাৎ মানুষের পূর্ণরূপে বেঁচে থাকার অধিকার এবং স্রষ্টাকে উপাসনা করার অধিকারের মধ্যে সমন্বয় চায়। মানুষের অস্তিত্বের যৌক্তিকতা এখানেই।
এই আলোকে মানুষের আত্মিক পরিশুদ্ধি এবং ব্যক্তিগতভাবে ও সমষ্টিগতভাবে তার নৈতিক ও বৈষয়িক উৎকর্ষের লক্ষ্যে ইসলাম ইবাদতের সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি নির্ধারণ করে দিয়েছে। এভাবে ইসলাম এমন এক সমাজ গড়তে চায় যেখানে ভ্রাতৃত্ব ও সম্প্রীতি বিরাজ করবে এবং এটা করতে গিয়ে ইসলাম সমাজ, সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশে বাধা সৃষ্টি করে না। তাই দেখা যায় নামাজ, রোজা ও হজ্জের মতো ফরজ ইবাদতগুলোর একই সাথে ব্যক্তিগত ও সামাজিক ভূমিকা রয়েছে। স্বভাবত এই দায়িত্বগুলো পালন করতে গিয়ে একজন মুসলমান জীবনের মূলস্রোত থেকেও বিচ্ছিন্ন হয় না আবার সমাজ থেকেও তাকে নির্বাসিত হতে হয় না। বরং ভাবগত ও বাস্তব ও উভয় দিক দিয়ে সমাজের সাথে তার সম্পর্ক আরো ঘনিষ্ট হয়। এ কারণে ইসলাম বৈরাগ্যবাদকে অনুমোদন করে না। আর বৈরাগ্যবাদ মানে সমাজ থেকে নির্বাসন। সেখানে স্বাভাবিক সামাজিক জীবনের স্পন্দন থাকে না। ইসলাম চায়, এই স্বভাবসম্মত সামাজিক জীবন যাপনের মাধ্যমে মানুষ পবিত্রতা অর্জন করুক। সমাজের উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে প্রতিটি মানুষ তার অবদান রাখুক। অর্থাৎ ইসলামের দৃষ্টিতে গোটা পৃথিবী মানুষের ধর্মীয় কর্মকান্ডের ক্ষেত্র। তাই সিরাতুল মুস্তাকীমের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ মানুষের প্রতিটি কাজই ইবাদত ও জিহাদ বলে গণ্য করা হয়। ইসলাম অন্যান্য ধর্ম ও দর্শনের মতো মানুষের জৈবিক চাহিদাকে অস্বীকার করে তথাকথিত আধ্যাত্মিক সাধনায় তাকে মোটেও উৎসাহিত করে না। দেহের দাবীকে অস্বীকার বা উপেক্ষা করে আত্মার পরিশুদ্ধির স্থান ইসলামে নেই। এ ব্যাপারে কুরআনের ঘোষনা দ্ব্যর্থহীন: “হে আল্লাহ, আমাদের ইহকালকে সুন্দর করুন এবং সুন্দর করুন আমাদের পরকালকে।” (২:২০১)
হাদীসেও আমরা একই বাণীর প্রতিধ্বনি শুনতে পাই: “হে আল্লাহ, আমার সকল কাজকর্মের হিফাযতকারী ধর্মকে সঠিকরূপে উপস্থাপিত করুণ; আমার জাগতিক কর্মকান্ডকে পরিশুদ্ধ করুণ যেখানে আমি জীবন নির্বাহ করি এবং আমার পরকালীন জীবনকেও পবিত্র করুণ এবং সার্বিক কল্যাণের লক্ষ্যে আমার জীবনকে প্রাচুর্যের উৎস বানিয়ে দিন এবং সকল অপকর্ম থেকে আমাকে রক্ষা করে আমার মৃত্যুকে শান্তির উৎসে পরিণত করুন।” (মুসলিম)
হাদীসে আরো বলা হয়েছে :\"তোমার ওপর তোমার দেহের অধিকার রয়েছে।” (সকল প্রামাণ্য সূত্রে সমর্থিত) তদুপরি কুরআনুল কারীমে পরিচ্ছন্নতা ও সৌন্দর্যকে উপেক্ষা করার প্রবণতা অনমোদন করা হয়নি বরং এটাকে বান্দার প্রতি আল্লাহর দান বলে উল্লেখ করা হয়েছে। মক্কায় অবতীর্ণ একটি আয়াতে আল্লাহ পাক বলছেন:“হে আদমের সন্তানেরা! সুন্দর পরিচ্ছদে ভূষিত হও সব সময় এবং নামাযের স্থানেও। খাও ও পান করো কিন্তু অপচয় করো না। আল্লাহ অপচয়কারীকে ভালবাসেন না।”
“বলুন, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জীবিকা সৃষ্টির জন্যে যেসব শোভন বস্তু এবং বিশুদ্ধ ও পবিত্র জীবিকা সৃষ্টি করেছেন তাকে কে নিষিদ্ধ করেছে?” (৭:৩২)
মদিনায় অবতীর্ণ একটি সূরায় আল্লাহ তায়ালা বিশ্বাসীদের সম্বোধন করে বলেছেন : “হে ঈমানদাররা! আল্লাহ তায়ালা যেসব উৎকৃষ্ট বস্তু তোমাদের জন্যে হালাল করেছেন তাকে তোমরা হারাম করো না এবং সীমালংঘন করো না। আল্লাহ সীমালংঘনকারীকে পছন্দ করেন না। আল্লাহ তোমাদেরকে যে হালাল ও উৎকৃষ্ট জীবিকা দিয়েছেন তা থেকে আহার করো আর আল্লাহকে ভয় করে চলো যাঁর প্রতি তোমরা ঈমান এনেছ।” (৫:৮৭-৮৮)
এসব আয়াতে ঈমানদারদের কাছে পবিত্রতা অর্জনের প্রকৃত ইসলামী পথ বাতলে দেয়া হয়েছে এবং অন্যান্য ধর্মে যেসব বাড়াবাড়ি রয়েছে সেরূপ প্রবণতা থেকে মুসলমানদেরকে নিবৃত করা হয়েছে। এই আয়াত দু’টির শানে নুযূলও এখানে লক্ষণীয়। একদল সাহাবী নিজেদেরকে খোজা করে দরবেশ হয়ে ঘুরে বেড়ানোর ইচ্ছে ব্যক্ত করলে এই আয়াত নাযিল হয়।
ইবনে আব্বাস (রা) বলেন: “একটি লোক রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে এসে বললেন: “হে আল্লাহর রাসূল, আমি যখনি এই গোশত গুলো খাই তখুনি আমার কামপ্রবৃত্তি মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে, তাই আমি গোশত না খাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।” এবং এরপর পরই আয়াত নাযিল হয়। আনাস ইবনে মালিক (রা) বর্ণনা করেন, “একদল লোক নবী সহধর্মিণীদের কাছে এসে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর এবাদত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। এ ব্যাপারে অবহিত হওয়ার পর তারা তাদের ইবাদত-বন্দেগীকে অপর্যাপ্ত বিবেচনা করে একজন বললেন, আমি সর্বদা সারারাত নাময পড়ব; আরেকজন বললেন, আমি সারা বছর রোজা রাখব এবং কখনো ভাঙ্গবো না। এ সময় আল্লাহর নবী তাদের কাছে এলেন এবং বললেন: “আল্লাহর শপথ আল্লাহর প্রতি আনুগত্য আমারই সবচেয়ে বেশী এবং তাঁকে বেশী ভয় করি তোমাদের চেয়ে; তথাপি আমি রোযা রাখি এবং ভাঙ্গিও, আমি ঘুমোই এবং নারীকে বিয়ে করি। সুতরাং যে আমার সুন্নাহকে অনুসরণ করে না সে আমার অনুসারীদের অন্তর্ভূক্ত নয়।”
প্রকৃতপক্ষে রাসূলুল্লাহ (সা) -এর সুন্নাহর মধ্যেই ইসলামের ধ্যান ধারণা এবং তার বাস্তব রূপায়নের সমগ্র চিত্র ফুটে উঠেছে। এতে আল্লাহর প্রতি, পরিবারের প্রতি, নিজের প্রতি, তথা প্রতিটি ক্ষেত্রে দায়িত্ব ও কর্তব্যের এক সুষম ও সমন্বিত রুপ মূর্ত হয়েছে।
ধর্মীয় চরমপন্থার ত্রুটি
বস্তুত সকল উগ্রতা ও বাড়াবাড়ির মধ্যে মারাত্মক ত্রুটি অন্তর্নিহিত থাকে। এ কারণে এর বিরুদ্ধে সতর্কতা বাঞ্ছনীয়। প্রথম ত্রুটি হচ্ছে সাধারণ মানবীয় প্রকৃতি বাড়াবাড়ির (excessivenes) সাথে সামঞ্জস্যশীল নয়; এই প্রকৃতি কোনো বাড়াবাড়িকে বরদাশত করতে পারে না। যদি মুষ্টিমেয় লোক স্বল্প সময়ের জন্যেও বাড়াবাড়ি সহ্য করতে পারে বৃহত্তর জনগোষ্ঠী তা করতে সক্ষম হবে না। আল্লাহর বিধান সমগ্র মানুষের জন্যে, মুষ্টিমেয় হঠকারীর জন্যে নয় যাদের তথাকথিত সহন ক্ষমতা বেশি বলে আপাতত প্রতীয়মান হয়। একবার রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর একজন বিশিষ্ট সাহাবী মুয়াযের ওপর ক্রদ্ধ হয়েছিলেন। কারণ তিনি নামাযের ইমামতিতে দীর্ঘ সময় ক্ষেপণ করেছিলেন বলে একজন মুসল্লী অভিযোগ করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে বললেন: “হে মুয়ায! তুমি কি মুসল্লীদের পরীক্ষা করছ? তিনি তিনবার এ কথার পুনরুক্তি করলেন।” (বুখারী) আরেকবার মহানবী (সা) অস্বাভাবিক ক্রুদ্ধ হয়ে একজন ইমামকে লক্ষ্য করে বললেন, “তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ ভাল কাজের (নামায) প্রতি মানুষের বিতৃষ্ণা সৃষ্টি কর। তাই তোমরা যখনি নামায পড়াবে তখন তা সংক্ষিপ্ত করা উচিত, কারণ মুসল্লীদের মধ্যে দুর্বল ও বৃদ্ধ এবং কর্মব্যস্ত লোক থাকে। ” (বুখারী) রাসুলুল্লাহ (সা) মুয়ায ও আবু মূসাকে ইয়ামানে প্রেরণের প্রাক্কালে এই উপদেশ দিয়েছিলেন:“(জনগণের কাছে ধর্মীয় বিষয়গুলো) সহজ করে তুলে ধরো, কঠিনরূপে নয়। একে অপরকে মান্য করো, বিভেদে লিপ্ত হয়ো না।” (সকল প্রামাণ্য সূত্রে সমর্থিত)
উমর ইবনে খাত্তাব (রা) এর ওপর জোর দিয়ে বলেছেন: “নামাযের ইমামতিতে দীর্ঘসূত্রিতা করে বান্দার কাছে তার কাজকে (আমল) এবং আল্লাহকে ঘৃণার পাত্রে পরিণত করো না”।
বাড়াবাড়ি দ্বিতীয় ত্রুটি হচ্ছে, এটি ক্ষণস্থায়ী। যেহেতু মানুষের সহ্য ক্ষমতা ও অধ্যবসায় স্বভাবত সীমিত তাই সহজে সে একঘেঁয়েমি অনুভব করে। দীর্ঘ সময় ধরে বাড়াবাড়িমূলক ক্রিয়াকর্মে লিপ্ত থাকা তার স্বভাব বিরুদ্ধ। এমন একটা সময় আসবে যখন সে ক্লান্ত হয়ে পড়বেই, দৈহিক ও মানসিক উভয় দিক দিয়ে। এমনকি স্বভাবসম্মত নূন্যতম কাজটিও সে পরিত্যাগ করবে। অথবা অতিরিক্ত আমলের উল্টো এমন এক পথ বেছে নেবে যা হবে শেষ পর্যন্ত চরম অবহেলা ও শৈথিল্যের শামিল। এমন কিছু লোকের সাথে আমার সাক্ষাৎ ঘটেছে যাদেরকে দৃশ্যত গোঁড়া ও কঠোর মনে হয়েছে। পরে আমি তাদের সম্পর্কে খোঁজ খবর নিয়ে জেনেছি যে, তারা হয় পথভ্রষ্ট হয়ে সম্পূর্ণ বিপরীত পথে চলতে শুরু করেছে কিংবা ন্যূনপক্ষে হাদীসে বর্ণিত হঠকারী চরিত্রের লোকদের মতো সবেগে পিছু হটে এসেছে। এ সম্পর্কিত হাদীসটি হচ্ছে: “যে (হঠকারী জল্লাদবাজ লোক) (নির্দিষ্ট) দূরত্বও অতিক্রম করতে পারে না এমনকি পারে না তার বাহনের পিঠটাকেও ঠিক রাখতে।” (জাবিরের সনদে আল-বাজ্জাজ)
রাসূলুল্লাহর (সা) আরেকটি হাদীসেও এরূপ ইঙ্গিত রয়েছে: “সেই সব সৎকর্মে প্রবৃত্ত হও যা সহজে সম্পন্ন করা যায়; কেননা আল্লাহ তায়ালা (পুরষ্কার দানে) ক্লান্ত হন না যতোক্ষণ না তুমি (নেক আমলে) ক্লান্ত ও অবসন্ন হও... এবং আল্লাহর কাছে সেই আমলই সবচেয়ে প্রিয় যা নিয়মিত সম্পাদন করা হয় তা যতই ছোট হোক না কেন।” (হযরত আয়েশার (রা) বরাতে বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ ও আন-নাসাঈ) ইবনে আব্বাস (রা) বলেন: “মহানবী (সা) -এর একজন সেবক দিনে রোযা রাখতেন আর সারা রাত নামায পড়তেন। রাসূলুল্লাহ (সা) কে এ বিষয়ে জানান হলে তিনি বললেন, “প্রতিটি কাজের একটি শীর্ষ বিন্দু থাকে এবং তাকে অনিবার্যভাবে অনুসরণ করে শৈথিল্য। যে তার স্বাভাবিক সরল জীবনে আমার সুন্নাহকে অনুসরণ করে সে সঠিক পথে আছে আর যে শৈথিল্যের কারণে অন্যের পথ নির্দেশ অনুসরণ করে সে (ভুল করল) এবং (আল্লাহ পাক প্রদত্ত সরল পথ থেকে) বিচ্যুত হলো।” (আল বাজ্জাজ)
আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বলেন: “ইবাদত-বন্দেগীতে লিপ্ত থাকতে থাকতে ক্লান্ত ব্যক্তিদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা) কে অবহিত করা হলে তিনি বললেন: ‘এটা হচ্ছে ইসলামের কঠোর অনুশীলন এবং আমলের সর্বোচ্চ পর্যায়। প্রতিটি গোঁড়া ক্রিয়াকলাপের একটি শীর্ষ পর্যায় থাকে এবং সেই সাথে থাকে অনিবার্য শৈথিল্য.. যার সহজ-সরল আমল কিতাব (কুরআনুল কারীম) ও সুন্নাহর আলোকে নিষ্পন্ন হয় সে-ই সঠিক পথের ওপর কায়েম থাকে আর যার অবসন্নতা অবাধ্যতায় পর্যবসিত হবে তার ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী।” (আহমাদ এবং আবু শাকির সমর্থিত)
ইবাদতের ক্ষেত্রে চরমপন্থা বর্জনের এবং মধ্যপন্থা অবলম্বনের কী চমৎকার তাগিদ এই হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) মুসলমানদেরকে দিয়েছেন! তিনি আরো বলেছেন: “ধর্ম খুব সহজ আর সে নিজের ওপর অতিরিক্ত বোঝা চাপিয়ে নেয় সে তা শেষ পর্যন্ত ধরে রাখতে পারে না। সঠিক পথে চলো (বাড়াবাড়ি বা অবহেলা কোনটাই না করে), (পূর্ণতার) নিকটবর্তী হওয়ার চেষ্টা করো এবং (তোমার সৎকর্মের পুরষ্কার লাভের জন্যে) সুসময়ের অপেক্ষা করো।” (বুখারী ও নাসাঈ, আবু হুরায়রা বর্ণিত)
তৃতীয়ত, হঠধর্মী বাড়াবাড়ি অন্যের অধিকার ও কর্তব্যকে বিপন্ন করে। এ প্রসঙ্গে একজন বুযুর্গ বলেন: “প্রত্যেক বাড়াবাড়ির মধ্যে কারো কারো অধিকার হারানোর বেদনা জড়িত আছে।” আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) ইবাদত-বন্দেগীতে এমন মশগুল থাকতেন যে, তার স্ত্রীর প্রতি কর্তব্যও উপেক্ষিত হচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) একথা জানতে পেরে বললেন, “হে আবদুল্লাহ, আমি কি শুনিনি যে, তুমি সারাদিন রোযা রাখো আর সারারাত বন্দেগী করো?” আবদুল্লাহ বলেন, “জী হ্যাঁ, আল্লাহর রাসূল! মহানবী (সা) বললেন, “এরূপ করো না, কয়েকদিন রোযা রাখো আবার কয়েক দিনের জন্যে ছিড়ে দাও, রাতে বন্দেগীও করো আবার ঘুমোতেও যাও। তোমার ওপরে তোমার শরীরের অধিকার আছে, তেমনি তোমার ওপরে তোমার স্ত্রীর দাবী আছে এবং তোমার ওপর তোমার অতিথিরও দাবী আছে......।” (বুখারী)
এ ব্যাপারে প্রখ্যাত সাহাবী সালমান ফারসী এবং তাঁর অন্তরঙ্গ আবু দারদার মধ্যেকার ঘটনাটিও প্রণিধানযোগ্য। রাসূলুল্লাহ (সা) সালমান ও আবু দারদার মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন কায়েম করে দিয়েছিলেন। একদা সালমান আবু দারদার বাড়িতে বেড়াতে গেলেন। দেখলেন আবু দারদার স্ত্রী উমআল দারদা জীর্ণবসন পরিহিতা। তিনি এর কারণ জিজ্ঞেস করলে উমআল দারদা বললেন আপনার ভাই দুনিয়াবী (সাজগোজে) আগ্রহী নন। ইতিমধ্যে আবু দারদা এলেন এবং সালমানের জন্যে খাবারের আয়োজন করলেন। সালমান তার সাথে আবু দারদাকে খেতে বললে তিনি বললেন, ‘আমি রোযা আছি’। তখন সালমান বললেন, ‘তুমি না খেলে আমিও খাব না।’ সুতরাং আবু দারদাও সালমানের সাথে খেলেন। রাতে আবু দারদা নামাযের জন্যে উঠলে সালমান তাকে ঘুমোতে যেতে বললেন। দারদা তাই করলেন। আবু দারদা পুনরায় শয্যাত্যাগ করলে সালমান আবার তাকে ঘুমোতে যেতে বললেন। শেষরাতে সালমান আবু দারদাকে উঠতে বললেন এবং উভয়ে নামায আদায় করলেন। পরে আবু দারদাকে সালমান বললেন, “তোমার ওপরে তোমার প্রভুর অধিকার আছে, তোমার ওপর তোমার আত্মার অধিকার আছে, তোমার ওপর তোমার পরিবারের অধিকার আছে, সুতরাং প্রত্যেককে তার ন্যায্য অধিকার দাও।” আবু দারদা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে এ ঘটনা বিবৃত করলেন। তিনি বললেন: “সালমান সত্য কথাই বলেছে।” (বুখারী ও তিরমিযী)
ধর্মীয় চরমপন্থার ধারণা
ধর্মীয় গোঁড়ামির প্রতিকার করতে হলে সর্বপ্রথমে এর সঠিক সংজ্ঞা, ব্যাখ্যা ও গভীর পর্যালোচনা প্রয়োজন। বিশুদ্ধ ইসলামী চেতনা ও শরীয়ার ভিত্তিতেই বিষয়টির বিচার বিশ্লেষণ করতে হবে। অন্য কোনো মানদন্ডে বিচার করলে তার কোনো মূল্য নেই, কেবল ব্যক্তিগত মতামতের কোন অবকাশ থাকতে পারে না। এ প্রসঙ্গে কুরআন বলছে: “যদি তোমাদের মধ্যে কোন বিষয়ে মতভেদ সৃষ্টি হয় তবে তা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কাছে পেশ করো যদি তোমরা আল্লাহ ও কিয়ামতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে থাকো।” (৪:৫৯)
মুসলিম উম্মাহর সমগ্র ইতিহাসে এ ব্যাপারে ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, মুসলমানদের মধ্যে বিভেদের বিষয় আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কাছে পেশ করার অর্থ হচ্ছে আল্লাহর কিতাব, আল কুরআন এবং মহানবী (সা)-এর সুন্নাহর মধ্যে এর সমাধান অন্বেষণ। শরীয়ভিত্তিক এরুপ অনুমোদন ছাড়া মুসলিম যুব সমাজ-যাদের বিরুদ্ধে চরমপন্থার অভিযোগ আনা হয়েছে-মুসলিম আলিমদের ফতোয়াবাজির প্রতি কর্ণপাত করবে না এবং তাদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ অস্বীকার করে যাবে। অধিকন্তু তারা প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধেই অজ্ঞতা ও মিথ্যাচারের অভিযোগ আনবে।
এখানে উল্লেখ্য, ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইদ্রিস আশ-শাফিঈর বিরুদ্ধে রাফেজী হওয়ার অভিযোগ আনা হয়েছিল। ক্ষুব্ধ হয়ে তিনি কোনো পরোয়া না করে এই সস্তা অভিযোগের বিরোধিতা করে একটি শ্লোক পাঠ করেন যার অর্থ হচ্ছে: “আহালে বায়েতের সকলের প্রতি ভালবাসাই যদি হয় প্রত্যাখ্যান তবে মানুষ ও জিনকে সাক্ষী করে বলছি যে, আমি একজন প্রত্যাখ্যানকারী।” বর্তমান যুগের একজন ইসলাম প্রচারক তার বিরুদ্ধে “প্রতিক্রিয়াশীলতার” অভিযোগ শুনে বলেন “কুরআন ও সুন্নাহর সুনির্দিষ্ট অনুসরনই যদি প্রতিক্রিয়াশীলতা তাহলে আমি প্রতিক্রিয়াশীল হিসেবেই বাঁচতে, মরতে ও পুনরুত্থিত হতে চাই।”
আসলে “প্রতিক্রিয়াশীলতা”, “অনমনীয়তা”,“গোড়ামী” ইত্যাদি শব্দের সঠিক সংজ্ঞা নিরূপণ করা অত্যাবশ্যক। তাহলেএক গ্রুপের বিরুদ্ধে আরেক গ্রুপের এসব শব্দের অপব্যবহার যেমন রোধ করা যাবে তেমনি ডান-বাম বলে পরিচিত বিভিন্ন বুদ্ধিজীবী ও সামাজিক মহল এসব শব্দের সুবিধাবাদী মনগড়া ব্যাখ্যাও দিতে পারবে না। একইভাবে “ধর্মীয় চরমপন্থা” শব্দটির সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা নির্ণীত না হলে সবাই নিজ নিজ মর্জি মাফিক এর প্রয়োগ করবে। ফলত মুসলিম সমাজে বিভেদ ক্রমবিস্তৃত হতে থাকবে আল-কুরআন ঘোষণা করেছে:
“যদি সত্য তাদের ইচ্ছা মাফিক নির্ধারিত হতো তাহলে আকাশ ও পৃথিবী এবং উভয়ের মধ্যস্থিত সব কিছু বিভ্রান্তি ও দুর্নীতি পূর্ণ হয়ে উঠতো।” (২৩:৭১)
এখন আমি দু\'টো গুরুত্বপূর্ন বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করবো। প্রথম, একটি মানুষের সাধুতার (piety) মাত্রা এবং যে পরিবেশের মধ্যে তিনি বাস করেন তা বহুলাংশে অন্য মানুষের প্রতি তার মনোভাব গঠনের প্রভাবিত করে থাকে। কঠোর ধর্মীয় পটভুমি থেকে গড়ে ওঠা একজন মানুষ কারো মধ্যে সমান্যতম বিচ্যুতি বা অবহেলা দেখলে সহ্য করতে পারেন না। তার দৃষ্টিতে বিচার করে তিনি যদি দেখেন যে এমন মুসলমানও আছে যারা তাহাজ্জুদ পড়ে না বা নফল নামায পড়ে না তবে তার বিষ্ময়ের ঘোর কাটতে বেশ সময় লাগবে বৈ কি। এটা ঐতিহাসিকভাবেই খাঁটি কথা। মানুষের আমল ও আখলাকের পরীক্ষা করলে দেখা যাবে, তাবেঈন এবং রাসূলুল্লাহ (সা) ও তাঁর সাহাবীদের নিকটবর্তী যুগের লোকদের আমলের তুলনায় পরবর্তী লোকদের (মুসলমানদের) আমল-আখলাক ততোটা উজ্জ্বল নয়। একটি প্রাবাদে আছে: “পরবর্তী লোকদের নেক কাজ পূর্ববর্তী লোকদের ত্রুটির সমতুল্য।” এখানে আনাস ইবনে মালিক (রা) তার সমসাময়িক তাবেঈনদের উদ্দেশ্যে যা বলতেন তা স্মর্তব্য “আপনারা তুচ্ছ জ্ঞান করে অনেক কাজ করছেন অথচ একই কাজ রাসূলুল্লাহ (সা) -এর আমলে ভয়ানক পাপ বলে গণ্য করা হতো।” একই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করতেন হযরত আয়েশা (রা)। তিনি বিখ্যাত কবি লাবিদ ইবনে রাবিয়ার একটি শ্লোক আবৃত্তি করতেন। তিনি তার এই শ্লোকে এই বলে বিলাপ করেছেন যে, সমাজে অনুকরণীয় সজ্জন ব্যক্তিদের অন্তর্ধানে যে শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে তা স্থান দখল করেছে ছন্নছাড়ারা যাদের সঙ্গ মামড়ি-পড়া পশুদের মতোই বিষাক্ত। হযরত আয়েশা (রা) এই ভাবে বিস্মিত হতেন যে লাবিদ আজ বেঁচে থাকলে বর্তমান সমাজের চেহারা দেখে কী মনে করতেন! হযরত আয়েশা (রা) -এর ভাগ্নে উরওয়াহ ইবনে আল জুবায়েরও এই শ্লোকটি আবৃত্তি করে ভাবতেন আজ হযরত আয়েশা (রা) ও বেঁচে থাকলে এ যুগের অধঃপতনকে কী চোখে দেখতেন! এবার আমরা এর উল্টোটা দেখি। যে ব্যক্তির ইসলাম সম্পর্কে তেমন জ্ঞান বা আনুগত্যবোধ নেই কিংবা সে এমন এক পরিবেশে গড়ে উঠেছে যেখানে শরীয়ত উপেক্ষিত বরং আল্লাহ যা নিষেধ করেছেন তাই করা হয় নিদ্বির্ধায়, সেই ব্যক্তি ইসলামের প্রতি কারো সামান্য অনুরাগ দেখলেই তাকে গোঁড়া বা চরমপন্থী বলে মনে করবে। এমন ব্যক্তি সাধুতার ভান করতে অভ্যস্ত এবং সে ধর্মের কোনো কোনো বিষয়ের সমালোচনা করেই ক্ষান্ত হবে না, এরা যৌক্তিকতাকেও অস্বীকার করে বসবে। ইসলামের প্রতি যারা অনুরক্ত তাদেরকে সে অভিযুক্ত করবে এবং কোনটা হারাম আর কোনটা হলাল সে বিষয়ে তর্ক করতে তার জুড়ি মেলা ভার। অবশ্য ইসলাম থেকে দুরত্বে অবস্থানের দরুনই এসব মানুষের এরুপ দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে। ভিন্ন আদর্শ ও জীবন ধারার প্রভাবের কারণে কোনো কোনো মুসলমানের কাছে পানাহার, সৌন্দর্যবোধ, শরীয়তের পাবন্দীর তাগিদ এবং ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্টার মতো সুষ্পষ্ট ইসলামী মূল্যবোধগুলো ধর্মীয় গোঁড়ামী বা চরমপন্থা ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না। এমন ব্যক্তির চোখে শ্বশ্রুমন্ডিত মুসলমান তরুণ কিংবা হিজাব পরা মুসলিম তরুণী মাত্রই চরমপন্থী। এমনকি ভাল কাজের আদেশ ও খারাপ কাজের নিষেধকে গোঁড়ামী এবং ব্যক্তি স্বাধীনতার হস্তক্ষেপ বলে মনে করা হয়। আমরা জানি আমাদের ধর্ম বিশ্বাসের মূল ভিত্তি হচ্ছে একমাত্র ইসলামকেই সত্য বলে মেনে নেয়া এবং যারা এটা বিশ্বাস করে না তারা বিভ্রান্ত বলে স্বীকার করা। কিন্তু এ সমাজে এমন মুসলমানও দেখা যায় যারা এটা মানতে নারাজ। যারা ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্মগ্রহণ করেছে তাদের কাফির গণ্য করতে তাদের ঘোরতর আপত্তি! এটাকেও তারা উগ্রতা ও গোঁড়ামী বলে মনে করে। আর এটা এমন একটা ইস্যু, যে ব্যাপারে আমরা কখনোই আপোস করতে পারি না।
দ্বিতীয়ত, কেউ জোরালো মতামত অবলম্বন করলেই তাকে “ধর্মীয় চরমপন্থী” বলে অভিযুক্ত করা অন্যায়। কেউ যদি তার মতামত সম্পর্কে স্থির নিশ্চিত হয় যে, এ ব্যাপারে শরীয়তেরও অনুমোদন রয়েছে তবে সে তার মত অনুযায়ী স্বাচ্ছন্দে চলতে পারে। তার পেছনে ফুকাহাদের সমর্থন দুর্বল বলে অন্যেরা মনে করলেও তাতে কিছু আসে যায় না। সে তো কেবল তার চিন্তা ও বিশ্বাসের জন্যে দায়ী। সে যদি ধর্মীয় বাধ্যবাধকতাকে সীমিত গন্ডিতে অনুশীলন না করে নিজের ওপর অতিরিক্ত বোঝা চাপিয়ে নেয়, কারো বলার কিছু নেই। কেননা সে হয়তো মনে করে অতিরিক্ত আমলের মাধ্যমে আল্লাহর রেজামন্দী হাসিল করা সহজ হবে। বস্তুত এসব বিষয়ে মত পার্থক্যের অবকাশ আছে। কেউ একটা বিষয়কে সহজভাবে নেয় আবার অনেকে এর বিপরীত আচরণে অভ্যস্ত। রাসূলে কারীম (সা) -এর সাহাবীদের বেলায়ও একথা সত্য। উদাহরণস্বরুপ, ইবনে আব্বাস (রা) ধর্মীয় বিষয়গুলোর প্রতি সহজতর দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করতেন, কিন্তু ইবনে উমর (রা) ছিলেন কঠোর মনোভাবাপন্ন। এই প্রেক্ষাপটে, একজন মুসলমানের পক্ষে যথেষ্ট হবে যদি সে কোনো একটি মাযহাবের অনুসরণ করে অথবা কুরআন ও সুন্নাহভিত্তিক নির্ভরযোগ্য ইজতিহাদের পন্থা অনুসরণ করে। অতএব যদি কেউ চার ইমাম যথা শাফিঈ, আবু হানিফা, মালিক ও আহমদ ইবনে হাম্বলের (রা) মাযহাবের মধ্যে কোনো একটি অনুসরণ করে এবং তা যদি অন্য কিছু পন্ডিতের বিবেচনায় সমকালীন মতের বিরোধী হয় তাহলেই কি ঐ ব্যক্তিকে চরমপন্থী বা গোঁড়া বলে অভিহিত করা সঙ্গত হবে? আমাদের কি কোনো অধিকার আছে অন্য কোনো ব্যক্তির ইজতিহাদী পন্থা বেছে নেয়ার অধিকারকে খর্ব করার?
বহু ফকীহ এই রায় দিয়েছেন যে, মুখমন্ডল ও হাত বাদ দিয়ে মুসলিম মহিলারা সমগ্র দেহকে আবৃত করে- এমন পোষাক পরতে পারে। হাত ও মুখমন্ডলকে ছাড় দেয়ার পক্ষে তারা কুরানের এই আয়াতকে প্রমাণ হিসেবে পেশ করেন: “..... তাদের সৌন্দর্য ও অলঙ্কার প্রদর্শন করা উচিত নয়, তা ব্যতীত যা (অবশ্যই সাধারণভাবে) দৃষ্টিগোচর হয়।” (২৪:৩১)
এর পক্ষে তারা হাদীসের প্রামাণ্য ঘটনা এবং ঐতিহ্যের সমর্থনও পেশ করেছেন। বহু সমকালীন আলেমও এই মতের সমর্থক, আমি নিজেও।পক্ষান্তরে, অনেক আলেম যুক্তি পেশ করে বলেছেন যে, হাত এবং মুখও ‘আওরা’ অর্থাৎ অবশ্যই ঢাকতে হবে। তারাও কুরআন, আল-হাদীস ও প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্য থেকে প্রমাণ পেশ করেন। সমসাময়িক বহু আলেম এই মতের সমর্থক। এদের মধ্যে পকিস্তান, ভারত, সউদী আরব ও উপসাগরীয় দেশের আলেমও রয়েছেন। তারা মুসলিম মহিলাদের মুখ ঢাকতে এবং হাত মোজা পরতে বলেন। এখন কোনো মহিলা যদি ঈমানের অঙ্গ হিসেবে এটা পালন করেন তবে তাকে কি গোঁড়া বলে চিহ্নিত করতে হবে? কিংবা কোনো ব্যক্তি যদি তার স্ত্রী কন্যাকে এটা মেনে চলার জন্য তাগিদ দেন তাহলে তাকেও কি চরমপন্থী বলে অভিহিত করতে হবে? আল্লাহর বিধান বলে কেউ যা মনে করে তা ছেড়ে দিতে কাউকে বাধ্য করার অধিকার কি আমাদের আছে? তা যদি করি তাহলে কি আমরা আমাদের খেয়ালখুশী চাপিয়ে দেয়া কিংবা চরমপন্থী বরে অভিযোগ এড়ানোর জন্যে আরেকজনকে আল্লাহর ক্রোধের দিকে ঠেলে দেয়ার অযাচিত নছিহত করব না? নাচ-গান, ছবি ও আলোকচিত্রের ব্যাপারে যারা কঠোর মনোভাব পোষণ করেন সে ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। এসব কঠোর মত আমার ব্যক্তিগত ইজতিহাদ থেকে শুধু নয় বরং অন্যান্য প্রখ্যাত আলেমদের ইজতিহাদ থেকেও ভিন্নতর। কিন্তু স্বীকার করতেই হয় যে এসব মতামতের সাথে প্রাথমিক যুগ ও সমসাময়িক অনেক আলিমদের দৃষ্টিভঙ্গির সাজুয্য রয়েছে।
আমরা অনেকে শার্ট ও প্যান্টের পরিবর্তে ছওব (ঢিলা জামা-কাপড়) পরা অথবা মেয়েদের সাথে মোসাফাহা না করাকে গোঁড়ামি বলে সমালোচনা করি; কিন্তু খোদ উসূলে ফিকাহ এবং উম্মাহর ঐতিহ্যের মধ্যেই এসব বিষয়ে বিতর্কের বীজ নিহিত রয়েছে। মতপার্থক্য থাকার সুযোগের কারণেই সমসাময়িক আলিমরা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মত প্রকাশ করেন এবং জোর প্রচার চালান। ফলত, আল্লাহর রহমতের আশা এবং তাঁর শাস্তির ভয়ে কিছু নিষ্ঠাবান মুসলিম তরুণ এসব বিষয় মেনে নেন। সুতরাং ফকীহর রায়ের ভিত্তিতে আল্লাহর সন্তষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে কেউ যদি ধর্মচর্চায় কঠোরতা অবলম্বন করে তবে সে জন্যে তাকে নিন্দা করা বা গোঁড়ামির অপবাদ দেয়া সমীচীন নয়। তার বিশ্বাসের পরিপন্থী আচরণে তাকে বাধ্য করার অধিকার আমাদের নেই। আমাদের একমাত্র কর্তব্য হচ্ছে প্রজ্ঞা, যুক্তি ও ধৈর্যের মাধ্যমে এমনভাবে তাকে বোঝানোর চেষ্টা করা যাতে আমরা যেটাকে সত্য বলে বিশ্বাস করি তা গ্রহণে সে উদ্বুদ্ধ হয়।
চরমপন্থার লক্ষণ
চরমপন্থার প্রথম লক্ষণ হচ্ছে অন্ধতা। চরমপন্থী বা গোঁড়া ব্যক্তি নিজের মতের প্রতি একগুঁয়ে ও অসহিষ্ণুর মতো এমন অটল থাকে যে, কোনো যুক্তিই তাকে টলাতে পারে না। অন্য মানুষের স্বার্থ, আইনের উদ্দেশ্য ও যুগের অবস্থা সম্পর্কে তার স্বচ্ছ ধারণা থাকে না। তারা অন্যের সাথে আলোচনায়ও রাজী হয় না যাতে তাদের মতামত অন্যের মতামতের সাথে তুলনামূলক পর্যালোচনা করা যায়। তাদের বিবেচনায় যা ভাল হয় কেবল তা অনুসরণেই তারা প্রবৃত্ত হয়। যারা অন্যের মতামত দাবিয়ে রাখা ও উপেক্ষা করার চেষ্টা চালায় এবং যারা এর জন্য তাদেরকে অভিযুক্ত করে, আমরা উভয়কেই সমভাবে নিন্দা করি। বস্তুতপক্ষে যারা নিজেদের মতকেই কেবল নির্ভেজাল বিশুদ্ধ এবং অন্যদেরকে ভ্রান্ত বলে মনে করে তাদেরকে কঠোরভাবে নিন্দা করা ছাড়া গত্যন্তর নেই বিশেষ করে তখন, যখন তারা কেবল ভিন্নমতের জন্যে প্রতিপক্ষকে জাহিল, স্বার্থন্বেষী, অবাধ্য তথা ফিসকের অভিযোগে অভিযুক্ত করে। তাদের আচরণে মনে হবে যেন তারাই নির্ভেজাল, খাঁটি বিশুদ্ধ এবং তাদের প্রতিটি কথাই যেন ওহী বা এলহাম! এ ধরণের একগুঁয়ে দৃষ্টিভঙ্গি উম্মাহর ইজমার পরিপন্থী। কেবলমাত্র কুরআন ও সুন্নাহ ছাড়া অন্য যে কোনো ব্যক্তির যে কোনো মত গ্রহণ বা বর্জন করা যেতে পারে। এটাই উম্মাহর সর্ববাদী সম্মত রায়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় কিছু লোক বিভিন্ন জটিল বিষয়ে নিজেদের ইজতিহাদের অধিকার প্রয়োগ করে খেয়ালখুশী মতো রায় দিয়ে থাকেন। কিন্তু সমকালীন বিশেষজ্ঞ আলিমদেরকে একক বা যৌথভাবে ইজতিহাদের অধিকার প্রয়োগ করতে দেখলে তারা বেজায় নাখোশ হন। অথচ ঐ সব ব্যক্তি কুরআন ও সুন্নাহর এমন হাস্যকর ব্যাখ্যা দেন যা আমাদের পূর্বপুরুষ বুজুর্গানে দ্বীন এবং সমসাময়িক আলিমদের রায় বা সিদ্ধান্তের পরিপন্থী। মজার ব্যাপার হচ্ছে, তারা নিজেদেরকে হযরত আবু বকর, উমর, আলী ও ইবনে আব্বাসের (রা) সমপর্যায়ের মনে করেন। তাদের এই উদ্ভট দাবীতে তেমন ক্ষতি ছিল না যদি তারা তাদেরকে কেবল সমসাময়িক পন্ডিতদের সমপর্যায়ের মনে করতেন।
সুতরাং নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে, চরমপন্থা বা গোঁড়ামির পরিস্কার লক্ষণ হচ্ছে অন্ধতা। তার দাবীর সারকথা: “বলার অধিকার কেবল আমার, তুমি কেবল শুনবে। আমি পথ দেখাবো, তুমি সেই পথে চলবে। আমার মত অভ্রান্ত, তুমি ভ্রান্ত। আমার ভুল হতে পারে না, আর তোমারটা কখনো ঠিক হতেই পারে না।” অর্থাৎ একজন তার অন্ধমতানুযায়ী কোনোভাবে অন্যের সাথে সমঝোতায় আসতে পারে না। অথচ আমরা জানি, সমঝোতা ছাড়া সমাজ সংহত হতে পারে না। সমঝোতা কেবল তখনই সম্ভব যখন কেউ মধ্যপন্থায় অবস্থান নেয়। কিন্তু একজন চরমপন্থী মধ্যপন্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, বিশ্বাস তো দূরের কথা। জনগণের সংগে তার সম্পর্ক পূর্ব ও পশ্চিমের সম্পর্কের মতো- যতই তুমি একটির নিকটে যাবে তুমি অন্যটি হতে দূরে সরে যাবে। বিষয়টি আরো জটিল হয়ে যায় যখন এ রকম ব্যক্তি অন্যকে বাধ্য করার মনোভাব গ্রহণ করে কেবল শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে, অনেক সময় অভিযোগের মাধ্যমে যে প্রতিপক্ষ অবিশ্বাসী, বিপথগামী কিংবা বেদাতী। এরূপ বুদ্ধিবৃত্তিক সন্ত্রাস শারীরিক সন্ত্রাসের চেয়েও ভয়ঙ্কর।
চরমপন্থার দ্বিতীয় পরিচয় হচ্ছে, সর্বক্ষণ বাড়াবাড়ি করার নীতিতে অটল থাকা এবং সমঝোতার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকা সত্ত্বেও অন্যকে তার মতো আচরণে বাধ্য করতে প্রয়াসী হওয়া যদিও তার কাজটি আল্লাহর বিধানসম্মত নয়। তাকওয়া ও সতর্কতার কারণেও এক ব্যক্তি ইচ্ছা করলে কোনো কোনো বিষয়ে কখনো কখনো কঠোর মত পোষণ করতে পারে। কিন্তু এটা এমন অভ্যাসে পরিণত হওয়া উচিত নয় যাতে সে যেখানে প্রয়োজন এমন ক্ষেত্রেও সহজ সরল বিষয়গুলো পরিহার করে। এরুপ দৃষ্টিভঙ্গি কুরআন ও হাদীসের শিক্ষার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। আল্লাহ বলেন: “আল্লাহ তোমাদের জন্যে যা সহজ তা চান, যা তোমাদের জন্যে ক্লেশকর তা চান না।” (২:১৮৫)
আল্লাহ রাসূলও (সা.) ইতিপূর্বে উদ্ধৃত হাদীসে বলেছেন: “(ধর্মীয় বিষয়গুলো) সহজ করে তুলে ধরো কঠিন করো না।” (সকল প্রামাণ্য সূত্রে সমর্থিত)
তিনি আরো বলেছেন : “তাঁর প্রদত্ত সুবিধা ভোগ করলে আল্লাহ খুশী হন যেমন (লোকেরা) তাঁর অবাধ্য হলে তিনি নারাজ হন।” (আহমাদ, বায়হাকী ও তাবারী) এছাড়া রেওয়ায়েত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) কে যখনি দু’টি কাজের মধ্যে একটি বেছে নিতে বলা হয়েছে, গর্হিত না হলে তিনি সহজতম পথটিই সর্বদা বেছে নিয়েছেন।” (বুখারী ও তিরমিযী)
মানুষের জন্যে কোনো কাজকে জটিল করে তোলা কিংবা তার ওপরে চাপ সৃষ্টি করা রাসূলুল্লাহ (সা) -এর উজ্জ্বলতম গুণাবলীর পরিপন্থী। এটি পূর্ববর্তী বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ এবং পরবর্তীকালে কুরআনুল কারীমেও উল্লেখ করা হয়েছে: “যিনি তাদের জন্যে পবিত্র বস্তু বৈধ ও উত্তম (পবিত্র) এবং অপবিত্র বস্তু অবৈধ করেন এবং মুক্ত করেন তাদেরকে তাদের গুরুভার হতে ও শৃংখল হতে যা তাদের ওপর ছিল।” (৭:১৫৭)
এ কারণে রাসূলুল্লাহ (সা) কেবল একাকী নামযকে দীর্ঘ করতেন। আসলে তিনি পা ফুলে না ওঠা পর্যন্ত সারা রাত ধরে নামায পড়তেন। কিন্তু যখন তিনি জামায়াতে ইমামতি করতেন তখন তাঁর অনুসারীদের সহ্য ক্ষমতা ও পরিস্থিতির বিচারে নামায সংক্ষিপ্ত করতেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, “যখন তোমাদের মধ্যে কেউ নামাযের ইমামতি করে তখন তা সংক্ষিপ্ত করা উচিত, কেননা সেখানে দুর্বল, রুগ্ন ও বৃদ্ধলোক থাকে; কিন্তু কেউ একাকী নামায পড়লে ইচ্ছা মতো দীর্ঘ করতে পারো।” (বুখারী)
আবু মাসুদ আল আনসারী বর্ণনা করেছেন যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলল, “হে আল্লাহর রাসূল, আমি সালাতুল ফজরে হাযির হই না, কেননা অমুক অমুক নামাযকে দীর্ঘ করে থাকে। ” রাসূলুল্লাহ (সা) অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, “হে মানুষেরা তোমরা মানুষকে উত্তম কাজের (নামায) প্রতি বিতৃষ্ণ করতে চাও? যখন কেউ নামায পড়াবে তখন তা সংক্ষিপ্ত করবে, কেননা সেখানে দুর্বল, বৃদ্ধ ও ব্যস্ত লোক থকে। ” আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, রাসূলুল্লাহ (সা) একইভাবে রাগন্বিত হয়েছিলেন যখন জানতে পারেন যে, মুয়ায (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন: “যখন আমি নামাযের জন্যে দাঁড়াই তখন আমি একে দীর্ঘ করার ইচ্ছা করি, কিন্তু শিশুর কান্না শুনে আমি নামায সংক্ষিপ্ত করি, কারণ আমি মাতাদের কষ্টে ফেলতে চাই না।”
অবশ্য করণীয় কাজগুলোর মতো ঐচ্ছিক কাজগুলো সম্পন্ন করার চাপ দেয়াটাও বাড়াবাড়ির শামিল। অনেক সময় মাকরুহাতের জন্যে এমনভাবে কৈফিয়ত তলব করা হয় যেন এগুলো মুহাররামাতের (হারাম সমূহের) অন্তর্ভূক্ত। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ যেসব কর্তব্য কর্মের সুষ্পষ্ট আদেশ দিয়েছেন কেবল সেসব ব্যাপারেই কৈফিয়ত তলব করা যায়। এর বাইরে অতিরিক্ত সকল ধরনের ইবাদতই ঐচ্ছিক। নিম্নোক্ত ঘটনাটি থেকে বোঝা যাবে এটাই রাসূলুল্লাহ্ (সা) -এর মত: একদা এক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ (সা) কে অবশ্য পালনীয় কাজ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি মাত্র তিনটি কাজের কথা উল্লেখ করলেন- নামায, যাকাত ও রোযা। এছাড়া আর কিছু করার আছে কিনা জিজ্ঞাসিত হয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা) না-বাচক জবাব দিলেন এবং বললেন যে, বেদুঈন ইচ্ছে করলে বেশী কিছুও করতে পারে। বেদুঈন বিদায় নেয়ার আগে প্রতিজ্ঞা করলো, রাসূলুল্লাহ (সা) যা কিছু বলেছেন তার চেয়ে বেশীও করবে না, কমও করবে না। মহানবী (সা) একথা শুনে বললেন, “যদি সে সত্য কথা বলে থাকে তবে সে সফল হবে, অথবা বলেছিলেন “তাকে জান্নাত মঞ্জুর করা হবে।” (বুখারী)
আজকের যুগে একজন মুসলমান যদি অবশ্য কর্তব্য কাজগুলো সম্পন্ন করে এবং মুহাররামাতের সবচেয়ে জঘন্য কাজ থেকে দূরে থাকে তবে তাকে ইসলামের অন্তর্ভূক্ত বলে গণ্য করা যায় যতক্ষণ পর্যন্ত সে আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি আনুগত্য বজায় রাখে। এমনকি যদি সে ছোটখাটো মুহাররামাতের কাজ করে ফেলে তবে দৈনিক পাঁচ ওয়াক্তের নামায, জুমা’র নামায ও রোযার বদৌলতে তার ছোট অন্যায়গুলোর কাফফারাহ হয়ে যাবে। কেননা কুরআন ঘোষণা করছে: “ভাল কাজ খারাপ কাজকে অবশ্যই মিটিয়ে দেয়।” (১১:১১৪)
আরেকটি আয়াতে আছে: “যদি তোমরা সবচেয়ে জঘন্য নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকো তবে আমরা তোমাদের সকল খারাপ কাজকে মুছে ফেলবো এবং তোমাদেরকে উচ্চ সম্মানের স্থানে আসীন করবো।” (৪:৩১)
একজন মুসলমান যদি কিছু বিতর্কমূলক বিষয় অনুসরণ করেন যার হালাল বা হারাম হওয়া সম্পর্কে আমরা নিশ্চিত নই অথবা এমন কিছু কাজ পরিত্যাগ করেন যার ওয়াজিব হওয়া বা মুবাহ হওয়া অনিশ্চিত, তাহলে কুরআন ও সুন্নাহর উপরিউক্ত প্রমাণের প্রেক্ষিতে তাকে কি আমরা ইসলাম বহির্ভূত বলে ঘোষণা করতে পারি: আর এ কারণেই আমি কিছু সাধু লোকের কঠোর মতের বিরোধী। তারা শুধু নিজেদের আচরণের মধ্যেই এই গোঁড়ামি সীমাবদ্ধ রাখেন না, অন্যকেও এতে অহেতুক প্রভাবিত করতে চান। আরো আপত্তি আছে। এসব লোক কোনো কোনো আলিমের বিরুদ্ধেও বিশেদগার করতে কুন্ঠিত হন না। অথচ এসব আলিম সত্যিকার অর্থে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে সাধারণ মানুষের ওপর অনর্থক চাপিয়ে দেয়া বিধি-নিষেধের বোঝা হালকা করতে চান।
চরমপন্থার আরেকটি লক্ষন হচ্ছে নির্দয় কঠোরতা। চরমপন্থীদের স্থানকালের বিবেচনা জ্ঞান নেই। নও-মুসলিমদের প্রতি অন্তত প্রাথমিক অবস্থায় নম্র আচরণ করা উচিত-সেই নও-মুসলিম মুসলিম অথবা অমুসলিম যে দেশেরই হোক। এমনকি ধর্মের প্রতি সদ্য অনুরক্ত মুসলমানদের প্রতিও সহৃদয় দৃষ্টি দেয়া দরকার। নব দীক্ষিত মুসলমানদের প্রথমেই ছোটখাট বিষয়গুলো মানতে বাধ্য করানো উচিত নয়। প্রথমে তাদেরকে মৌলিক বিষয়গুলো বোঝার সুযোগ দিতে হবে। তাদের ধ্যান-ধারণা, চিন্তাধারা ইসলামের আলোকে সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে। একবার তাদের মনে ঈমানের চেতনা বদ্ধমূল হয়ে গেলেই ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভ এবং ক্রমান্বয়ে বাস্তব জীবনে আল্লাহর বিধি বিধান রূপায়ণের তাগিদ সৃষ্টি করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জীবন থেকে আমরা এর সত্যতা খুঁজে পাই। হযরত মুয়ায (রা) কে ইয়ামেনে পাঠানোর সময় হযরত মুহাম্মদ (সা) বলেছিলেন, “তুমি আহলে কিতাবের একটি জনগোষ্ঠীর কাছে যাচ্ছ। সেখানে পৌঁছে তাদেরকে এই সাক্ষ্য দিতে বলবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মা’বুদ নেই। এবং হযরত মুহাম্মদ (সা) তাঁর প্রেরিত রাসূল। যদি তারা এটা মেনে নেয় তখন তাদেরকে বলবে যে, আল্লাহ দিনে রাতে পাঁচ বার নামায আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন। তারপর বলবে যে, আল্লাহ তোমাদের মধ্যে ধনীদের কাছ থেকে যাকাত আদায় করে গরীবদের মধ্যে বন্টনের আদেশ দিয়েছেন। ........ (সকল প্রামাণ্য সূত্রে সমর্থিত)
মুয়ায (রা)- এর প্রতি রাসুলুল্লাহ (সা)-এর উপদেশের মধ্যে দাওয়াতী কাজের ক্রমিক পদ্ধতি লক্ষণীয়। উত্তর আমেরিকা সফরের সময় আমি কিছু নিষ্ঠাবান মুসলিম তরুণের আচরণে ক্ষুব্ধ হয়েছিলাম। এই তরুণরা একটি মুসলিম গ্রুপের সাথে সংশ্লিষ্ট। সেখানে মুসলমানরা সাধারণত শনি ও রবিবারের ভাষণের সময় চেয়ারে বসতো। ঐ তরুণরা মনে করে মাদুরে কেবলামুখী হয়ে বসা উচিত। এছাড়া শার্ট প্যান্টের পরিবর্তে ঢিলেঢালা পোষাক পরিধান এবং ডাইনিং টেবিলের পরিবর্তে মেঝেতে বসে খাওয়া উচিত। বিষয়টির ওপর তরুণেরা বিতর্কের ঝড় তুলেছিলো। উত্তর আমেরিকার মতো জায়গায় এরূপ দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণ দেখে আমি ক্ষুব্ধ না হয়ে পারিনি। সুতরাং আমি আমার ভাষণে বললাম : এই বস্তুবাদী সমাজে আপনাদের প্রধান কাজে হওয়া উচিত তাওতীদ ও আল্লাহর বন্দেগীর দিকে মানুষকে আহবান করা এবং পরকাল ও মহান ইসলামী মূল্যবোধের প্রতি তাদের আগ্রহ সৃষ্টি করা। সেই সাথে বৈষয়িক উন্নতির শীর্ষে আরোহণ করেও এই দেশগুলো যে জঘন্য ক্রিয়াকলাপে নিমজ্জিত তার পরিণতি সম্পর্কেও তাদের হুঁশিয়ার করে দিতে হবে। ধর্মীয় আচার-আচরণ ও খুঁটিনাটি বিষয়ে পদ্ধতিগত উৎকর্ষ অর্জনের বিষয়টি স্থান ও কালের প্রেক্ষাপটে বিচার করা উচিত। এর আগে আমাদের নিশ্চিত করতে হবে যে, ধর্মের মৌলিক ও অত্যাবশ্যক নীতিমালা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
আরেকটি ইসলামী কেন্দ্রের ঘটনা উল্লেখ করছি। মসজিদে ঐতিহাসিক ও শিক্ষামূলক চলচ্চিত্র প্রদর্শনী নিয়ে সেখানে বেশ হৈ চৈ হচ্ছিল। প্রদর্শনীর বিরোধীরা অভিযোগ করছেন যে, মসজিদকে সিনেমা হলে পরিণত করা হয়েছে। কিন্তু তারা একথা বেমালুম ভুলে বসেছেন যে, মসজিদের উদ্দেশ্য হচ্ছে মুসলমানদের আধ্যাত্মিক ও জাগতিক উভয় ক্ষেত্রের কর্মকান্ডের কেন্দ্রস্থল হিসেবে এক ব্যবহার করা। হযরত মুহাম্মদ (সা) -এর আমলে মসজিদ ছিলো একাধারে দাওয়া, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক কার্যক্রমের সদর দফতর। এটা সম্ভবত সকলেরই জানার কথা, আবিসিনিয়া থেকে আগত একদল লোককে রাসূলুল্লাহ (সা) মসজিদের মধ্যস্থলে বশা দিয়ে ক্রিয়া প্রদর্শনের অনুমতি দিয়েছিলেন এবং হযরত আয়েশা (রা) তা দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন। (বুখারী এবং অন্যান্য)
গোঁড়ামির চতুর্থ লক্ষণ হচ্ছে, মানুষের প্রতি আচার-আচরণে অশিষ্টতা, উপস্থাপনায় স্থুলতা এবং দাওয়াতী কাজে গোবেচারা ভাব। এসবই হচ্ছে কুরআন ও সুন্নাহর শিক্ষার সাথে সঙ্গতিহীন। আল্লাহ তায়ালা কুশলী ও মধুর ভাষায় ইসলামের প্রতি মানুষকে আহবান করার আদেশ দিয়েছেন: “হিকমতের সাথে ও সদুপদেশ দ্বারা তোমার প্রভুর দিকে (মানুষকে) আহবান জানাও এবং সদ্ভাবে (উৎকৃষ্টতম ও সুবিবেচনা প্রসূত পন্থায়) তাদের সাথে আলোচনা করো।”(১৬:১২৫)
রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রসঙ্গ টেনে কুরআন বলছে: “এখন তোমাদের কাছে তোমাদের মধ্য থেকে একজন রাসূল এসেছেন। তোমাদেরকে যা বিপন্ন করে তা তার জন্যে বেদনাদায়ক, তিনি তোমাদের মঙ্গলকামী, ঈমানদারদের প্রতি তিনি দয়াময় ও করুণাশীল।” (৯:১২৮।
আল কুরআনুল কারীমে সাহাবীদের সাথে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সম্পর্কের রূপ বর্ণনা করে বলা হয়েছে: “আল্লাহর রহমতে আপনি তাদের প্রতি কোমল হৃদয় হয়েছিলেন, আপনি যদি কর্কশ ও কঠোর হৃদয়ের হতেন তাহলে তারা আপনার কাছ থেকে সরে পড়তো।” (৩:১৫৯)
আল কুরআনে মাত্র দুটি ক্ষেত্রে দৃঢ়তা ও কঠোরতার উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমত, যুদ্ধেক্ষেত্রে। যুদ্ধ বিজয় অর্জনের লক্ষ্য দৃঢ়তা ও কঠোরতার অত্যাবশ্যক। এক্ষেত্রে প্রয়োজনে কোমলতা পরিহার করতে হবে অন্তত যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত। কুরআন বলছে, “সেসব অবিশ্বাসীর বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাও, তারা তোমাদের মধ্যে কঠোরতা দেখুক।” (৯:১২৩)
দ্বিতীয়ত, শরীয়তের বিধান অনুযায়ী অপরাধীর শাস্তি কার্যকর করার ব্যাপারে। সেক্ষেত্রে আল্লাহর আইন প্রয়োগের বেলায় নমনীয়তার কোনো অবকাশ নেই। কুরআনের ভাষায়: “ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণী তাদের প্রত্যেককে এক শত বেত মারো। আল্লাহর বিধান কার্যকর করতে তাদের প্রতি দয়া যেন তোমাদেরকে প্রভাবাম্বিত না করে, যদি তোমরা আল্লাহ ও কিয়ামতে বিশ্বাসী হও। ” (২৪:২)
কিন্তু দাওয়াতী কাজের ব্যাপারে সহিংসতা ও কঠোরতার কোনো অবকাশ নেই। এই হাদীসে তার প্রমাণ পাওয়া যায়: “আল্লাহ সকল ব্যাপারে দয়া পছন্দ করেন এবং দয়া সবকিছু সুন্দর করে, সহিংসতা সবকিছু ত্রুটিপূর্ণ করে।” এছাড়া আমাদের বুজর্গ পূর্বপুরুষরাও একথা বলেছেন, “যারা ভাল কাজের আদেশ দিতে চায় তারা যেন তা নম্রতার সাথে করে। ” সহিংসতা আল্লাহর পথে দাওয়াতী কাজের উদ্দেশ্যকেই পন্ড করে দেয়। দাওয়াতী কাজের লক্ষ্য হচ্ছে মানুষের হৃদয় কন্দরে আলোর রশ্মিপাত করা, যে আলোর পরশে তার ধ্যান-ধারণা, চিন্তাধারা, আবেগ-আচরণ রূপান্তরিত হয়ে তাকে একটা নতুন সত্তা হিসেবে সৃজন করবে। সে আল্লাহ্ দ্রোহী থেকে পরিণত হবে একজন আল্লাহ ভিরু ব্যক্তিত্বে। দাওয়াতী কাজ একইভাবে সমাজের প্রচলিত বিশ্বাস, ঐতিহ্য ও পদ্ধতির ভিত্তিমূলে নাড়া দিয়ে তাকে নতুনরূপে গড়তে চায়।
এসব মহান উদ্দেশ্য অর্জন করতে হলে প্রজ্ঞা ও সহৃদয়তা অত্যাবশ্যক। তদুপরি প্রয়োজনে মানুষের প্রকৃতির দিকে লক্ষ্য রাখা। মানব প্রকৃতিতে একগুঁয়েমি, পরিবর্তন বিরোধিতা ও তর্কপ্রিয়তা অন্তর্নিহিত। দাওয়াতী কাজের সময় এই প্রকৃতির মোকাবিলা করার একমাত্র হাতিয়ার হচ্ছে নম্র, কোমল ও কৌশলময় আচরণ। এই হাতিয়ার ব্যবহার করেই উদ্দিষ্ট ব্যক্তির হৃদয়ের মণিকোঠায় স্থান করে নিতে হবে।ফলত তার প্রকৃতি যতোই অনমনীয় হোক এক সময় তাকে নমনীয় হতেই হবে। তার অহঙ্কার-অহমিকা অমায়িকতায় রূপান্তরিত হবেই। আলকুরআন আমাদেরকে এই প্রক্রিয়া অবলম্বেনের দিকেই নজর দিতে বলেছে। এছাড়া পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণ ও তাঁদের উম্মতরা একই প্রক্রিয়ায় দাওয়াতী কাজ চালিয়েছেন। হযরত ইবরাহীম (আ) তাঁর পিতা ও জনগণের প্রতি, শুয়াইব(আ) তাঁর জনগোষ্ঠীর প্রতি, হযরত মূসা (আ) ফেরাউনের প্রতি তথা সূরা ইয়াসিনে (৩৬:২০) উল্লিখিত সাধারণ মানুষের প্রতি ঈমানদারদের দাওয়াতী কাজ একই পন্থায় সম্পন্ন হয়েছে। আর সব দাওয়াতী কাজের মূল কথা ছিলো একটি: তোমরা আল্লাহর বন্দেগী কবুল করো। একজন ঈমানদার যখন তার সমগোত্রীয়দের আল্লাহর পথে দাওয়াত দেন তখন তার মধ্যে সমমর্মিতার আকুল আবেগ প্রতিধ্বনিত হয়। ফেরাউনের প্রতি একজন ঈমানদারের দাওয়াতের মধ্যেও সেই ব্যঞ্জনা ফুটে উঠেছে: “হে আমার স্বজাতি! আজ তোমাদেরই কর্তৃত্ব, দেশে তোমরাই প্রবল; কিন্তু আল্লাহর আযাব যখন আমাদের ওপর আপতিত হবে তখন আমাদেরকে কে সাহায্য করবে? (৪০:২৯)
অতঃপর তিনি আল্লাহর বাণীর প্রতি কর্ণপাত না করার পরিণামে অতীতের জাতিসমূহকে কিভাবে আযাব ভোগ করতে হয়েছে তা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন: “হে আমার স্বজাতি! আমি তোমাদের জন্যে পূর্ববর্তী সম্প্রদায়সমূহের শাস্তির দিনের অনুরুপ দুর্দিনের আশঙ্কা করি যেমন ঘটেছিলো নূহ, আদ, সামূদ ও তাদের পূর্ববর্তীদের ক্ষেত্রে। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের ওপর কোন অবিচার করতে চান না।” (৪০: ৩০-৩১)
এর পর তিনি কেয়ামত দিবসের ভয়াবহতা সম্পর্কে বর্ণনা দিয়ে বলছেন--
“হে আমার স্বজাতি! আমি তোমাদের জন্যে সেই কিয়ামত দিবসের ভয় করছি যেদিন তোমরা পরস্পরকে ডাকবে (এবং বিলাপ করবে); কিন্তু সেদিন তোমরা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পালাতে থাকবে। আল্লাহর তরফ থেকে সেদিন তোমাদেরকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না। আল্লাহ যাকে বিভ্রান্ত করেন তার জন্যে কোন পথপ্রদর্শক নেই।” (৪০:৩২-৩৩)
এভাবে আমরা দেখি একজন নবী মিনতি সহকারে নম্র ও কোমল ভাষায় দাওয়াত দিয়ে চলেছেন যার মধ্যে হুঁশিয়ারি আছে, আশার প্রেরণাও আছে:
“হে আমার কওম! আমাকে অনুসরণ করো। আমি তোমাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করবো। ইহকালীন জীবন (অস্থায়ী) উপভোগের বস্তু এবং একমাত্র পরকালীন আবাসই স্থায়ী- এবং হে আমার কওম! কী আশ্চর্য! আমি তোমাদেরকে মুক্তির দিকে আহবান করছি আর তোমরা আমাকে জাহান্নামের দিকে ডাকছ! তোমরা আমাকে বলছ আল্লাহকে অস্বীকার করতে এবং তাঁর সাথে শিরক করতে যার সম্পর্কে আমার কোন জ্ঞান নেই; আর আমি তোমাদেরকে সেই সর্বশক্তিমানের দিকে আহবান করছি যিনি ক্ষমাশীল।” (৪০: ৩৮-৪২)
অতঃপর তিনি উপদেশ বাণী দিয়ে শেষ করছেন: “(এখন) আমি যা বলছি অচিরেই তা তোমরা স্মরণ করবে। আমি (আমার) যাবতীয় বিষয় আল্লাহতে অর্পণ করছি; আল্লাহ তাঁর বান্দাদের উপর সর্বদা দৃষ্টি রাখেন।” (৪০:৪৪)
বস্তুত এই পদ্ধতিই সমকালীন ইসলামী কর্মীদের দাওয়াতী কাজ চালিয়ে যাওয়া উচিত যাতে তারা একগুঁয়ে ও অন্য ধর্মের লোকদের প্রতিকূল প্রকৃতির সাথে মুকাবিলা করতে পারে। ফেরাউনের কাছে প্রেরণের সময় মূসা ও হারুন (আ)-এর প্রতি আল্লাহ যে উপদেশ দিয়েছিলেন তাতেও একই সুর ধ্বনিত : “তোমরা দ’জনেই ফেরাউনের কাছে যাও। কেননা সে সকল সীমা লংঘন করেছে। তোমরা তার সাথে নম্রভাবে কথা বলবে সম্ভবত সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা ভয় করবে (আল্লাহকে)।” (২০: ৪৩-৪৪)
অতএব হযরত মূসা (আ) ভদ্রভাবে ফেরাউনকে সম্বোধন করে বললেন, “তোমার কি আগ্রহ আছে যে, তুমি পবিত্র হও এবং আমি তোমাকে তোমার প্রভুর পথে পরিচালিত করি যাতে তুমি তাঁকে ভয় করো।” (৭৯: ১৮-১৯)
এই দৃষ্টিতে এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই যে, দাওয়াতী কাজে অভিজ্ঞ লোকেরা ভিন্নমতাদর্শী লোকদের সাথে আলাপ-আলোচনার সময় কোনো কোনো তরুণের অসহিষ্ণু আচরণকে সুনজরে দেখেন না। মানুষকে আল্লাহর পথে ডাকার সময়ে এরা প্রায়ই কর্কশ ও ক্ষিপ্ত আচরণ করে থাকে। ছোট-বড়, মাতা-পিতা, শিক্ষক, অভিজ্ঞ বুযুর্গ প্রমুখের সাথে কথা বলা বা আচরণের ব্যাপারে তাদের মান মর্যাদার দিকেও খেয়াল করা হয় না। মেহনতি মানুষ নিরক্ষর ও বিভ্রান্ত ব্যক্তিদের সাথে সম্পর্ক ও আচরণে তেমন তারতম্য দেখা যায় না। আবার রয়েছে এমন সব ব্যক্তি যারা শুধু বিদ্বেষবশত ইসলামের বিরোধিতা করে জ্ঞানের অভাবে। মোটকথা সকল শ্রেণীর লোককে তাদের নিজস্ব অবস্থানের দিকে লক্ষ্য রেখে সুযোগ ও সুবিধা মতো দাওয়াত দিতে হবে। কিন্তু আমদের সমাজে এখন এরুপ দূরদৃষ্টিসম্পন্ন লোকের বড়ই অভাব। প্রাথমিক যুগের হাদীস বিশেষজ্ঞরা অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে এ দিকে ইঙ্গিত করেছেন। যেসব রাবী নিজের রেওয়ায়েত নিয়ে আত্মপ্রচারে নেমে পড়তেন তাদের রেওয়ায়েত মুহাদ্দিসরা গ্রহণ করেননি। বরং তাদেরটাই গ্রহণ করেছেন যারা নিজেদের উদ্ভাবন সম্পর্কে ছিলেন প্রচারভিমুখ। সন্দেহ ও অবিশ্বাসও গোঁড়ামির একটি লক্ষণ। চরমপন্থীরা তাৎকষণিকভাবে একজনকে অভিযুক্ত করে বসে এবং সঙ্গে সঙ্গে রায় দিতেও তারা পারঙ্গম! “দোষ প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত একজন নির্দোষ”-এ প্রবাদটির তারা থোড়াই পরোয়া করে। তারা সন্দেহ করা মাত্র একজনকে দোষী সাব্যস্ত করে ফেলে, ব্যাখ্যা ছাড়াই উপসংহারে উপনীত হয়। তাদের দৃষ্টিতে কারো সামন্য ত্রুটি যেন মাত্রা ছাড়িয়ে যাওয়ার শামিল! সোজা কথা, ভুলেই পাপ, পাপেই কুফরী! এ ধরণের প্রতিক্রিয়া ইসলামের শিক্ষার চরম লংঘন ছাড়া আর কিছু নয়। অথচ ইসলাম চায় এক মুসলমান আরেক মুসলমানের আয়না হয়ে পরস্পরকে সংশোধন করুক; বিনম্র ও ক্ষমাশীল ব্যবহারের মধ্য দিয়ে অন্যের আচরণ ও জীবন যাত্রায় উৎকর্ষতা আনুক।
কেউ যদি ঐসব চরমপন্থীদের সাতে দ্বিমত পোষণ করে, তবে তার ধর্ম বিশ্বাস ও চরিত্রের সাধুতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়। তার মত ইসলামের দৃষ্টিতে সঠিক হলেও তাকে সীমালংঘনকারী বিদয়াতী, এমনকি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সুন্নাহর অমর্যাদাকারী বলেও চিহ্নিত করা হয়। এপ্রসঙ্গে অনেক নজীর উল্লেখ করা যায়। আপনি যদি বলেন লাঠি বহন করা বা মেঝেয় বসে খাওয়ার সাতে সুন্নাহর কোনো সম্পর্ক নেই তাহলে আপনাকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর অমর্যাদাকারী বলতে বিন্দুমাত্র বিলম্ব হবে না। অভিজ্ঞ মুসলিম মনীষী ও আলিমরাও এ অভিযোগ থেকে রেহাই পান না। কোনো ফকীহ যদি মুসলমানদের সুবিধা হতে পারে এমন কোনো ফতোয়া দেন তবে তার বিরুদ্ধে ধর্মীয় ব্যাপারে শৈথিল্যের অভিযোগ আনা হবে। যদি কোনো মুবাল্লিক যুগোপযোগী পদ্ধতিতে মানুষকে ইসলামের দাওয়াত দেন তবে তাকে পাশ্চাত্য সভ্যতার ভক্ত বলে অপবাদ দেয়া হবে। শুধু জীবিত নয়, মৃত ব্যক্তিরাও অভিযোগের হাত থেকে রেহাই পান না। অর্থাৎ চরমপন্থীদের সাথে দ্বিমত পোষণ করলেই আর রক্ষা নেই। নির্বিচারে তাকে ফ্রিম্যাসন, জাহমী অথবা মুতাযিলী বলে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হবে। এখানেই শেষ নয়, ইসলামের চার মহান ফকীহর বিরুদ্ধেও চরমপন্থীরা নির্দ্বিধায় বিষেদগার করতে কসুর করেনি।
প্রকৃতপক্ষে হিজরী চতুর্থ শতকের মুসলিম উম্মাহর সমগ্র ইতিহাসকে আক্রমনের লক্ষ্য বস্তু করা হয়। অথচ এ কালটা নজীরবিহীন সভ্যতা ও গৌরভময় অবদানের জন্যে অবিস্মরণীয়। চরমপন্থীরা এই যুগটাকে সমসাময়িক সকল অশুভ কর্মকান্ডের উৎসস্থল বলে মনে করে। কেউ কেউ এটাকে ব্যক্তিগত ক্ষমতা দ্বন্ধ সংঘাতের যুগ বলে বিশ্বাস করে। আবার কেউ বলে এটা অজ্ঞাত ও কুফরীর যুগ। এই ধ্বংসাত্মক প্রবনতা নতুন কিছু নয়। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর যামানায়ও চরমপন্থীদের অস্তিত্ব ছিল। একদা জনৈক চরমপন্থী আনসার গনিমতের মাল বণ্টনে রাসূলল্লাহ (সা)-এর বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ এনেছিলো। আধুনিক চরমপন্থীদের মারত্মক দোষ হলো সংশয়। তারা যদি কুরআন ও সুন্নাহকে সঠিকভাবে হৃদয়ঙ্গম করতো তাহলে দেখতো যে, মুসলমানদের অন্তরে পারস্পারিক বিশ্বাস ও আস্থা সৃষ্টি করাই ইসলামের লক্ষ্যে। কোনো মুসলামানের উচিত নয় আরেক মুসলমানের গুণগুলো উপেক্ষা করে তার ছোট-খাট ত্রুটিগুলো বড় করে দেখা। কুরআন বলছে: “অতএব, আত্মপ্রশংসা করো না। তিনিই সবচেয়ে ভাল জানেন কে পরহেযগার।” (৫৩:৩২)
বস্তুত ইসলাম দুটি বিষয়ে মানুষকে কঠোরভাবে হুঁশিয়ার করে দিয়েছে: আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া এবং অপরকে সন্দেহ করা। আল্লাহ তায়ালা বলেন, “হে ঈমানদারগণ! বহুবিধ অনুমান থেকে দূরে থাকো, কারণ অনুমান কোনো কোনো ক্ষেত্রে পাপ।” (৪৯:১২)
রাসূলূল্লাহ (সা) এ প্রসঙ্গে বলেন, “সংশয় থেকে দূরে থাকো, কেননা সংশয় হচ্ছে কোনো কথাবার্তার মিথ্যা দিক।” (সকল প্রমাণ্য সূত্রে সমর্থিত)
ঔদ্ধত্য, অন্যকে ঠকানোর মনোবৃত্তি ও ঘৃণা থেকেই সংশয়ের উৎপত্তি। এগুলো হচেছ অবাধ্য আচরণের প্রথম ভিত্তি আর অবাধ্যতা হচ্ছে শয়তানী কাজ। শয়তান এই দাবী করেছিলো, “আমি তাঁর (আদমের) চেয়ে ভাল।” (৩৮:৭৬)
আর এজন্য সে হযরত আদম (আ) কে সিজদা করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলো। এ ধরণের অহঙ্কারের পরিণতি সম্পর্কে হুঁশিয়ারী পাওয়া যায় এই হাদীসে:“তুমি যদি শোন যে, কেউ বলছে মানুষ ধ্বংস হয়ে গেছে তাহলে বৃথা দম্ভের জন্যে সে নিজেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।” (মুসলিম)
আরেকটি রেওয়াতে আছে : “..... সে নিজেই তাদের ধ্বংসের কারণ।” অর্থাৎ তাঁর সন্দেহ ও অহঙ্কার এবং আল্লাহর রহমত থেকে তাদেরকে নিরাশ করানোই (ধ্বংসের কারন) এমন একটি প্রবণতা যা অবয়ের সূচনা করে এবং মুসলিম মনীষীরা একে “মনের রোগ” বলে চিহ্নিত করেছেন। রাসূলুল্লাহ(সা) ও এ ব্যাপারে আমাদেরকে সতর্ক করে দিয়েছেন, “তিনটি মারাত্মক পাপ আছে- অতিরিক্ত লোভ, কামনা ও অহঙ্কার।” মুসলমান তার কোনো কাজেই অহঙ্কার করতে পারে না। কেননা সে তো এ ব্যাপারে কখনোই নিশ্চিত হতে পারে না যে, আল্লাহ তার আমল মঞ্জুর করবেন। আল্লাহ দাতা ব্যক্তিদের সম্পর্কে আলকুরআনে বলেছেন: “এসব লোক ভীতিপূর্ণ হৃদয়ে দান-খয়রাত করে। কারণ তারা তাদের প্রভুর কাছে ফিরে যাবে।” (২৩:৬০)
হাদীস শাস্ত্রে কুরআনের এই আয়াতের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে যে এরা হচ্ছে সেই সব সৎকর্মশীল লোক যারা এই ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকে যে, তাদের আমল আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নাও হতে পারে। ইবনে আতা বলেন: “আল্লাহ তোমার জন্যে আনুগত্যের দুয়ার খুলে দিতে পারেন। কিন্তু গ্রহনযোগ্যতার দ্বার নাও খুলতে পারেন। তিনি তোমাকে অবাধ্য হওয়ার পরিস্থিতির মধ্যে ফেলতে পারেন (যাতে তুমি অনুতপ্ত হয়ে) আবার সঠিক পথে ফিরে আসতে পারো। অবাধ্যতার ফলশ্রুতিতে যে বিনয়াবনত চিত্তের উন্মেষ হয় তা অহংকার ও উদ্ধতপূর্ণ সাধুতার চেয়েও উত্তম।” হযরত আলী ইবনে আবু তালিবের (রা) বাণীতে আমরা বর্ণনার প্রতিধ্বনি পাই : “ যে ভাল কাজ মানুষের মনে অহংকার আনে তার চেয়ে আল্লাহ তার উপর মুসিবতকেই পছন্দ করেন।” ইবনে মাসুদ বলেন, “ধ্বংসের দু’টি প্রধান লক্ষণ হচ্ছে অহঙ্কার ও নৈরাশ্য। অধ্যবসায় ও সংগ্রাম ছাড়া সুখ অর্জন করা যায় না। একজন অহংকারি ব্যক্তি অধ্যবসায়ী হতে পারে না। কারণ সে নিজেকে পূর্ণতাপ্রাপ্ত বলে মনে করে। আর হতাশ ব্যক্তি কোনো চেষ্টাই চালায় ন। কারণ এটাকে সে অর্থহীন মনে করে।”
আবার আসুন দেখা যাক চরমপন্থার চরম রূপ কী। চরমপন্থী গ্রুপ অন্য সকল মানুষের শান্তি ও নিরাপত্তার অধিকারী অস্বীকার করে। অতএব প্রতিপক্ষকে হত্যা এবং তার বিষয় সম্পত্তি ধ্বংস করার পন্থা বেছে নেয়। এই অবস্থা তখন সৃষ্টি হয় যখন চরমপন্থী গ্র“প তাদের বাইরে অন্য সকলকে কাফির বলে ভাবতে শুরু করে। এ ধরনের চরমপন্থার ফলে বাকী সমস্ত উম্মাহর সাথে তাদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। প্রাথমিক যুগে খারিজীরা ঠিক এমনিফাঁদে পড়েছিলো। অথচ তারা নামায, রোযা ও কুরআন তিলাওয়াতের মতো ধর্মীয় রীতিনীতি পালনে অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ছিলো। কিন্তু তাদের চিন্তাধারা ছিলো বিকৃত। তাদের বিশ্বাস ও আচরণে প্রচন্ড গোঁড়ামীর দুরুন অনিচ্ছা সত্ত্বেও সহজ সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছিলো। রাসূলুল্লাহ (সা) এদের সম্পর্কে আভাস দিয়েছিলেন এভাবে: “তাদের (আলখাওয়ারিজ) নামায, কিয়াম ও তিলাওয়াতের তুলনায় তোমাদের মধ্যে কারো নামায, কিয়াম ও তিলাওয়াত অনুল্লেখযোগ্য মনে হবে।” তথাপি তিনি তাদের সম্পর্কে বলেন, “তারা কুরআন তিলাওয়াত করবে। কিন্তু গলার বাইরে যাবে না এবং কোনো রকম স্বাক্ষর ছাড়াই তারা ধর্মের পথ অতিক্রম করবে।” (মসলিম)
রাসূলুল্লাহ (সা) আরো বলেন, “তারা মুসলমানদেরকে খতম করা এবং মুশরিকদের রক্ষা করা তাদের কর্তব্য বলে মনে করবে।” (মসলিম)
এ কারণে কোনো মুসলমান খারিজীদের হাতে পড়লে নিজেকে আল্লাহর বাণী ও কিতাব সম্পর্কে জানতে আগ্রহী মুশরিক বরে পরিচয় দিতো। একথা শুনে খারিজীরা তাকে প্রাণে বাঁচাতো এবং নিরাপদে গন্তব্য স্থানে পৌঁছার ব্যবস্থা করে দিতো। তাদের কার্যকলাপের সমর্থনে তারা কুরআনের এই আয়াতকে প্রমাণ হিসেবে দাখিল করতো: “কোনো মুশরিক আশ্রয় চাইলে তাকে আশ্রয় দাও, যাতে সে আল্লাহর বাণী শুনতে পায়, তারপর তাকে তার নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দাও। কারণ তারা জ্ঞান রাখে না।” (৯:৬)
পরিতাপের বিষয় এই যে, আটক লোকটি যদি স্বীকার করতো যে, সে মুসলমান তবে তাকে খারিজীরা হত্যা করতো। দুর্ভাগ্যজনক যে, কোনো কোনো মুসলমান এসব ঘটনা থেকে শিক্ষা নেননি। জামায়াত আত-তাকফির আল-হিজরা মনে হয় খারিজীদের পদচিহ্ন ধরেই এগোচ্ছে। যারা পাপ করে সঙ্গে সঙ্গে তওবা করে না তাদেরকে এই জামায়াত কাফির বলে মনে করে। যেসব শাসক শাসন কাজে শরীয়ত প্রয়োগ করেন না এবং যেসব শাসিত এদের আনুগত্য করে উভয়েই এদের চোখে ধিক্কৃত। আর যেসব আলিম উভয় পক্ষকে কাফির বলে নিন্দা করেন না তারাও ধিক্কৃত। যারা এই গ্রুপের কর্মসূচী প্রত্যাখ্যান করে কিংবা চার ইমামের অনুসরণ করে তাদেরকেও এরা কাফির বলে মনে করে। কেউ যদি তাদের দলে গিয়ে কোনো কারণে দল ত্যাগ করে তবে তাকে মুরতাদ বলে অবশ্যই হত্যা করা হবে। তারা ৪র্থ শতাব্দীর পরবর্তী যুগকে অজ্ঞতা ও কুফরীর যুগ বলে অভিহিত করে। এভাবে এই গ্রুপ কুফরীর অপবাদ দিতে এতোই পারঙ্গম যে, এদের হাত থেকে জীবিত মৃত কেউই রেহাই পায় না। বস্তুত এভাবে এই গ্রুপ গভীর পানিতে পড়েছে। কেননা কাউকে কুফরীর অপবাদ দেয়ার পরিণতি মারাত্মক। তার জীবন ও সম্পত্তির বাজেয়াপ্তি তখন আইনসিদ্ধ হয়ে যায়। তার সন্তান ও স্ত্রীর ওপর অধিকার থাকবে না; সে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হবে, কেউ তার উত্তরাধিকারীও হতে পারবে না; তার দাফন ও জানাযা নিয়েও সমস্যা সৃষ্টি হবে। কেননা তাকে মুসলমানদের গোরস্তানে জায়গা দেয়া যায় না ইত্যাদি ইত্যাদি!
রাসূলুল্লাহ(সা) বলেছেন, “যখন কোনো মুসলমান আরেক মুসলমানকে কাফির বলে তখন তাদের মধ্যে নিশ্চয় একজন তাই।” (বুখারী)
এর অর্থ, কুফরীর অভিযোগ প্রমাণিত না হলে যে অভিযোগ আনবে তার ওপরেই ঐ অভিযোগ বর্তাবে, যার মানে হচ্ছে ঐ ব্যক্তি দুনিয়া ও আখিরাতে কঠিন মুসিবতের সম্মুখীন হবে। উসামা বিন জায়িদ বলেন: “যদি কোনো ব্যক্তি বলে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, তাহলে ইসলামের মধ্যে দাখিল হলো এবং (ফলত) তার জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা পেয়ে গেলো। কিন্তু যদি সে ভয়ে কিংবা তলোয়ারের মুখে একথা বলে তবে তার জওয়াবদিহি আল্লাহÍ কাছেই তাকে করতে হবে। কেবল দৃশ্যমান ঘটনারই আমরা (বিচার) করতে পারি।” (বুখারী)
হযরত উসামা (রা) এক যুদ্ধে এক ব্যক্তি কলেমায়ে শাহদাত উচ্চারণ করার পরেও তাকে হত্যা করেছিলেন। ঐ ব্যক্তির গোত্র যুদ্ধে পরাজিত হয়েছিলো। রাসূলুল্লাহ (সা) এ কথা জানতে পেরে উসামার (রা) কাছে কৈফিয়ত তলব করেন। তখন তিনি বলেন, “আমি মনে করেছিলাম ঐ ব্যক্তি হয়তো আশ্রয়ের আশায় এবং ভীত হয়ে কলেমা পাঠ করেছে। ” রাসূলুল্লাহ (সা) জিজ্ঞেস করলেন, “আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই-এই স্বীকারোক্তির পরেই কি তুমি তাকে হত্যা করেছিলে? উসামা (রা) বর্ণনা করেন, “রাসূলুল্লাহ (সা) বার বার আমাকে এই প্রশ্ন করতে লাগলেন যতোক্ষণ না আমার মনে হলো এই দিনটির আগে আমি ইসলাম গ্রহণই করিনি।”
শরীয়ত আমাদেরকে এই শিক্ষা দেয় যে, যারা সচেতনভাবে ও স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেছে, সাক্ষ্য ও ঘটনাবলী দ্বারা সুপ্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত তাদেরকে ইসলাম থেকে বহিস্কৃত করা যাবে না। খুন, ব্যভিচার, মদ্যপান ইত্যাদির মতো কবীরা গুনাহ করলেই কারো বিরুদ্ধে কুফরীর অভিযোগ আনা যাবে না-অবশ্য এতটুকু দেখতে হবে যে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির শরীয়তের প্রতি অস্বীকৃতি বা অশ্রদ্ধা আছে কিনা। এ কারণে ঠান্ডা মাথায় হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তির আত্মীয় ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজনের মধ্যেও কুরআন ভ্রাতৃপ্রতিম সম্পর্ক স্থাপন করতে চায়। কুরআন বলছে: “তবে তারা ভাইয়ের তরফ থেকে কাউকে কিছু মাফ করে দেয়া হলে প্রচলিত নিয়মের অনুসরণ করবে এবং সততার সাথে তাকে তা প্রদান করতে হবে।” (২:১৭৮) যারা একজন মদ্যপায়ীকে অভিশাপ দিয়েছিলো তাদের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন: “তাকে অভিশাপ দিও না। সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা) কে ভালবাসে।” (বুখারী)
ঐ মদ্যপায়ী ইতিপূর্বে কয়েকবার মদ্যপানের অভিযোগে শাস্তি ভোগ করেছিলো। উপরন্তু খুন, ব্যভিচার ও মদ্যপানের মতো অপরাধের জন্যে শরীয়ত ভিন্ন ভিন্ন রকম শাস্তির বিধান করেছে। এগুলো যদি কুফরই হতো তবে তো তাদেরকে রিদ্দার (ইসলাম ত্যাগের) বিধি মুতাবিক দন্ড দেয়া হতো!
চরমপন্থীরা যেসব দুর্বোধ্য বায়বীয় প্রমাণের ভিত্তিতে অভিযোগ খাড়া করে, কুরআন ও সুন্নাহর মৌলিক ও দ্ব্যর্থহীন ভাষ্যে তা খন্ডন করা হয়েছে। এই বিষয়টি বহু শতাব্দী পূর্ব থেকে একটি মীমাংসিত বিষয়, অতএব এর পুনরুজ্জীবন প্রচেষ্টা নিরর্থক।
পরিভাষা সঙ্কেত
ইজমা : ইসলামী আইনের সূত্র হিসেবে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত।
আত-তাবিঈ : রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাহাবীদের সান্নিধ্য লাভকারী।
হিজাব : নারীর ইসলামী পোষাক।
আওরাহ : নারী-পুরুষের দেহের সেই অংশ বা শরীয়ত মতে অবশ্যই আবৃত রাখতে হবে।
ফাসাকা : পাপের কাজ।
আল-মুন্দুব : যে আইন ও কাজ অনুমোদিত।
কিয়াস : ইসলামী আইনের উৎস, কুরআন ও হাদীসের আলোকে যুক্তিপূর্ণ সিদ্ধান্ত।
রিদ্দাহ : (বিশেষণ, মুরতাদ) আল্লাহর আনুগত্য এবং ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিত্ব শপথপূর্বক প্রত্যাহর।
দ্বিতীয় অধ্যায়
চরমপন্থার কারণ
চরমপন্থা বা গোঁড়ামী বিক্ষিপ্ত ঘটনাবলী থেকে উৎপন্ন হয়নি। এর অবশ্যই কারণ ও উদ্দেশ্য আছে। সকল প্রণীর মতো ঘটনা ও কার্যাবলী ও শূন্য থেকেউদ্ভব হয় না- বীজ ছাড়া যেমন চারা হয় না। প্রতিটি ঘটনার পেছনে থাকে কার্যকারণ। এটা আল্লাহর সৃষ্টিরও রীতি (সুনাম)। কোনো রোগের প্রতিকার করতে হলে প্রথমে দরকার রোগ নির্ণয় (ডায়াগনোসিস)। আবার এর জন্যে অত্যাবশ্যক হচ্ছে রোগের কার গুলো জানা আর কারণ জানা না গেলে রোগের ডায়াগনোসিস অসম্বম- অন্তত খুব কষ্টকর। এ কথা স্মরণ রেখেই আমরা চরমপন্থর (গোড়ামীর) কারণ ও উদ্দেশ্য নির্ণয়ে প্রয়াসী হবো। এখানে চরমপন্থা শব্দটি গুলু অর্থাৎ ধর্মীয় বাড়াবড়ির সমার্থবোধক।
প্রথমেই আমাদেরকে বুঝতে হবে যে, কোনো একটা মাত্র কারণ গোঁড়ামী বিস্তারের জন্যে সামগ্রিকভাবে দায়ী নয়। এটা একটা জটিল অদ্ভুত বিষয়। এর পেছনে নানা পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত কারণ রয়েছে। এগুলোর কোনো কোনোটি প্রত্যক্ষ, কোনোটি পরোক্ষ, কোনোটির গোড়া সূদুর অতীতে আবার কোনোটির উৎপত্তি বর্তমানে। সুতরাং একটি বিশেষ কারণের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে অনান্য কারণগুলো উপেক্ষা করা ঠিক হবে না। কোনো কোনো মতের প্রবক্তারা এরূপ একপেশে দৃষ্টি ভঙ্গি নিয়ে বিচার বিশ্লেষণে অভ্যস্ত। উদাহরণস্বরূপ মনোবিজ্ঞানী, বিশেষত মনস্তত্ত্ববিদরা অবচেতন মন থেকে উদ্ভূত কারণগুলোর ওপর গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। অন্যদিকে সমাজ বিজ্ঞানীরা সামজিক ও পরিবেশগত প্রভাবের মুখে মানুষের অসহায়ত্বের দিকে ইঙ্গিত দেন। তাদের দৃষ্টিতে মানুষ হচ্ছে সমাজের হাতে বন্দী প্রাণহীন পুতুল। ঐতিহাসিক বস্তুবাদের প্রবক্তারা যুক্তি দেখান, অর্থনৈতিক শক্তিই ঘটনাবলীর স্রষ্টা এবং এটাই ইতিহাসের গতডি পরিবর্তন করে।
পক্ষান্তরে আরেক দল অপেক্ষাকৃত ব্যাপক ও ভারসাম্যময় দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেন। তাদের মতে কারণসমূহ অত্যাধিক জটিল ও পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। এগুলো নানবিধ ক্রিয়া উৎপন্ন করে এবং একটা থেকে আরেকটার রূপ ভিন্ন। কিন্তু শেষ বিশ্লষণে এগুলোর প্রভাব অনস্বীকার্য। গোঁড়ামির কারণসমূহ ধর্মীয়, রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, মানসিক, বুদ্ধিবৃত্তিক অথবা সবগুলোর সমন্বয়ও হতে পারে। পরিবারের সদস্যদের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে অথবা গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে সমাজে অথাৎ সেই সমাজের বিশ্বাস ও আচরণ,কল্পনা ও বাস্তব, ধর্ম ও রাজনৈতিক, কথা ও কাজ, আকাঙ্ক্ষা ও সাফল্য অথবা দ্বীন ও দুনিয়ার অসংগতির মধ্যে এর কারণসমূহ বিদ্যমান থাকতে পারে। স্বাভাবিকভাবে এসব পরস্পর বিরোধিতা বৃদ্ধরা মেনে নিলেও তা সাময়িকমাত্র।
ক্ষমতাসীন সরকারের দুর্নীতির দরুনও চরমপন্থা বিস্তার লাভ করতে পারে। তাদের স্বেচ্ছাচারিতা, স্বার্থপরতা, তোষামোদপ্রিয়তা, মুসলিম উম্মাহর শত্রুদের প্রতি সেবাদাসবৃত্তি, স্বদেশের জনগণের অধিকার হরণ ইত্যাদি মানুষের মাঝে চরমপন্হী মনোভাবের জন্ম দেয়। মারাত্মক ব্যাপার হচ্ছে, এ ধরনের ক্রিয়াকলাপ শেষ পযর্ন্ত ধর্ম ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক ছিন্ন করেছে।
গোঁড়ামির আরেকটি প্রধান কারন হচ্ছে, দ্বীন সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব অথাৎ এর উদ্দেশ্যে ও মূল চোতনার গভীর তাৎপর্য উপলদ্ধিতে ব্যর্থতা। এই উপলদ্ধির অর্থ সার্বিক অজ্ঞাতাকে বোঝায় না। সার্বিক অজ্ঞতা বাড়াবাড়ি বা গোঁড়ামির জন্ম দেয়। আসলে অল্পবিদ্যা হচ্ছে ভয়ঙ্করী। এসব লোক মনে করে সেসব কিছু জানে এবং নিজেই যেন ফকীহ। আসলে সে নানা অজীর্ণ জ্ঞানের জগাখিচুড়ি। সে বিভিন্ন খন্ডের রূপ এবং তার সাথে অখন্ডের সম্পর্ক নির্ণয়ে ব্যার্থ। ফলে তার সামগ্রিক দৃষ্টভঙ্গি কখনো পরিচ্ছন্ন হতে পারে না। অতএব তার পক্ষে কনো সুনির্দৃষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অসম্ভব। এমন ব্যক্তি যদি নিজেকে ফকীহ বলে দাবী করে তাহলে দীনের অবস্থা কী হবে! ইমাম আবু ইসহাক আশ-শাতিবী তার আল-ইতিশাম গ্রন্থে অল্পবিদ্যার বিপদ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছেন। বিদআত এবং মুসলিম উম্মাহর অনৈক্যের মূল কারণ হলো আত্মজ্ঞানের অহঙ্কার, বিশেষ করে ধর্মীয় বিষয়ে তার যথেষ্ট জ্ঞান আছে মনে করে কেউ যখন ইচ্ছা মাফিক ইজতিহাদ শুরু করে রায় দিতে থাকে তখন তাকে অবশ্যই মুবতাদী (নতুন কিছু উদ্ভাবনকারী) বলতে হবে। রাসূলুল্লাহ (সা) এ ধরনের লোক সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছেন: “আল্লাহ জ্ঞান কেড়ে নেন না জনগনের (হৃদয়) থেকে। কিন্তু যখন কোনো আলিম থাকে না তখন তিনি তা কেড়ে নেন এবং জনগণ অজ্ঞ লোকদেরকে তাদের নেতা বানাবে যারা জ্ঞান ছাড়াই রায় দেবে, সুতরাং তারাও বিপথগামী হবে, জনগণকেও বিপথগামী করবে।” (বুখারী)
এ থেকে বিজ্ঞাজনেরা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, খাঁটি আলিমরা জনগণকে বিভ্রান্ত করেন না। কিন্তু তাদের অভাবে আলিমের বিশ্বাসভাজন কখনোই বিশ্বাস ভঙ্গ করে না, কিন্তু বিশ্বাসঘাতক তা পারে। এর সাথে যোগ দিয়ে বলা যায় খাঁটি আলিম কখনোই বিদআতের জন্ম দেয়। আনাস ইবনে মালিক (রা) বর্ণনা করেন, রাবিয়া একদিন খুব কাঁদছিলেন। তার ওপর কোনো মুসিবত এসেছে কিনা জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, “না, এ জন্যে কাঁদছি যে, মানুষ তাদের কাছ থেকে ফতোয়া তালাশ করেছে যাদের কোনো জ্ঞান নেই।”
বস্তুত সার্বিক অজ্ঞতার চেয়ে অহংকারযুক্ত অল্পবিদ্যার পন্ডিত কখনোই তার সীমাবদ্ধতাকে স্বীকার করে না। এদের একটি লক্ষণ হলো এরা আক্ষরিক অর্থের প্রতি বেশী জোর দেয়, তাৎপর্য ও উদ্দেশ্য উপলব্ধির চেষ্টা করে না। আলজাহিরিয়া মতাবরম্বীরা এ ধরনের পণ্ডিতী করতো। তারা আত-তালিল ও কিয়াস অগ্রাহ্য করতো।
“সমকালীন জাহিরিয়া” মতালম্বীরা পূর্বসূরীদের পথ ধরে যুক্তি প্রদর্শন করে যে, বাধ্যতামূলক কাজকর্মের কোনো গভীর অর্থ খোঁজা উচিৎ নয়। অবশ্য নব্যজাহিরিয়ারা পূর্বসূরীদের মতো তালিল পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান করে না। আমার ও অন্যান্য আলিমের মতে ইবাদত হচ্ছে এমন বাধ্যতামূলক কর্তব্য যার কারণ ও উদ্দেশ্য কখনোই বিশ্লেষণযোগ্য নয়। তবে যেসব শিক্ষা আমাদের জীবনকে নিয়ন্ত্রন করতে চায় সেগুলো অবশ্যই বিশ্লেষণ করতে হবে।
সুতরাং কোনো মুসলমান দান-খয়রাত করে বলে তার হজ্জ করা উচিত কিংবা হজ্জের সময় কুরবানীর অর্থ সদকা করে দেয়া উচিত-এই দাবী করা ভুল হবে। তেমনিভাবে এটাও অচিন্তনীয় যে, আধুনিক কর যাকাতের স্থান দখল করবে, রমযানের পরিবর্তে অন্য যে কোনো মাসে রোযা কিংবা শুক্রবারের স্থলে অন্য যে কোনো দিন জুমআ’র নামায আদায় করা যাবে। এসব বাদ দেওয়া যাবে না। এগুলো সবই মুসলমানের জন্যে অবশ্য পালনীয়। কিন্তু এ ধরনের আনুষ্ঠানিক ইবাদত প্রক্রিয়া ব্যতীত অন্য যে কোনো বিষয়ের কারণ ও উদ্দেশ্য আমরা বিশ্লেষণ করতে পারি এবং সঠিক উপলব্ধির পর ইতিবাচক অথবা নেতিবাচক সিদ্ধান্ত নেয়া যেতে পারে।
এখন আমরা কতিপয় প্রামাণিক বিষয় পর্যালোচনা করতে পারি:
ক. একটি বিশ্বস্ত হাদীসে বলা হয়েছে, কাফিরের দেশে কুরআন শরীফ নিয়ে যাওয়া উচিত নয়। এই নিষেধাজ্ঞার কারণ পরীক্ষা করলে দেখা যাবে, কাফিররা কুরআনের ক্ষতি বা অবমাননা করতে পারে এই আশংকায় রাসূলুল্লাহ (সা) এরূপ আদেশ দিয়েছেন। এরূপ আশংকা না থাকলে যেখানে ইচ্ছে কুরআন শরীফ নেয়া যেতে পারে। তাছাড়া দাওয়াতী কাজের জন্যে এটা তো অপরিহার্য।
খ. আরেকটি হাদীসে মাহরাম (অথাৎ বিষয় অযোগ্য পুরুষ আত্মীয়) সঙ্গী ছাড়া মুসলিম নারীকে সফর করতে নিষেধ করা হয়েছে। নারীর নারাপত্তা ও সফরের কষ্ট লাঘবই এর উদ্দেশ্য। আধুনিক যুগে যেহেতু সফরের এতো ঝুঁকি নেই তাই কোনো স্বামী তার স্ত্রীকে গাড়িতে তুলে দিতে পারেন। গন্তব্য স্থানে কোনো মাহরাম ব্যক্তি তাকে স্বাগত জানালে দোষের কিছু নেই। বস্তুত রাসূলুল্লাহ (সা) যোগাযোগ ব্যবস্থার এরূপ উন্নতির আভাস দিয়ে বলেছিলেন, এমন এক সময় আসবে যখন মানুষ এক আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় না করেই ইরাক থেকে মক্কা ভ্রমন করতে পারবে।
গ. রাসূলুল্লাহ (সা) দীর্ঘ অনুপস্থিতির পর রাতে বাড়ি ফেরা নাষিদ্ধ করেছেন। তিনি নিজেও সক্লে বা সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরতেন। এর দু’টো কারণ। প্রথম, আকস্মিকভাবে স্বামীর রাতে বাড়ি ফেরার মধ্যে স্ত্রীর প্রতি অবিশ্বাস ইসলাম সমর্থন করে না। দ্বিতীয়ত, স্ত্রী যেন নিজেকে পরিপাটি করে রাখতে পারে সে জন্যে স্বামীর আগমনের সময় জানার অধিকার তার আছে। কিন্তু এখন এসব আনুষ্ঠানিকতার সুযোগ খুব কম। মানুষের যাতায়াতের সময়সূচী মেনে চলতে হয়। কে কখন কোথায় যাবে তা আগেভাগেই নিশ্চিত করে বলা যায় না। তবে বাড়ি যাওয়া আগে টেলিফোন বা চিঠিতে জানানো উচিত। সুতরাং আমাদেরকে স্থান ও কালের প্রেক্ষাপটে উক্ত নিষেধাজ্ঞার কারণ ও উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ করতে হবে।
যাকাতকে ইবাদত মনে না করে অনেকে এটাকে কেবল অর্থ ব্যবস্থার অংশ হিসেবে গণ্য করতে চান। যাকাত ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এবং ধর্মীয় কর্তব্য। এটা ইসলামী শরীয়ত ব্যবস্থার একটি তাৎপর্যপূর্ণ ও স্থায়ী আয়ের সূত্র, সেই হিসেবে ইসলামী অর্থ ব্যবস্থারও স্তম্ভ। তাই এটার বাধ্যবাধকতাকে খর্ব করার কোনো উপায় নেই। যাকাতের সামাজিক সম্ভাবনার দিকে লক্ষ্য করে সকল মাযহাব-এর আহকামের ব্যপারে যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আমি ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বাস করি, ফসলের (ফল ও শস্য) দ অথবা পাঁচ ভাগ গরীবদের দান করা বাধ্যতামূলক- সে ফসল শুকনোই হোক আর তাজা হোক। সামাজিক অর্থনৈতিক বিকাশ হচ্ছে - এর মূল লক্ষ্য। ধনীর সম্পদে গরীবের সুনির্দিষ্ট হিস্যা আছে। আর এর লক্ষ্য হচ্ছে পবিত্রতা ও বিশুদ্ধতা: “তাদের সম্পদ থেকে তুমি সাদকা গ্রহন করো। এর দ্বারা তুমি তাদেরকে পরিশুদ্ধ ও পবিত্র করবে।”
একজন আধ্রনিক পন্ডিত “খাদ্যশস্যের ওপর সাদকা নেই” এই হাদীস উদ্ধৃত করে উপরোল্লিখিত যুক্তি অস্বীকার করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আমলে খাদ্যশস্যের ওপর যাকাতের বিধান প্রচলিত ছিল না বলেও তিনি দাবী করেন। কিন্তু হাদীসটি দুর্বল বিধায় তার যুক্তি মিথ্যা এবং বলেছেন এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহর (সা) কোনো প্রামাণিক হাদীস নেই। দ্বিতীয় যুক্তিটিও দু’টি কারণে মিথ্যা। প্রথম কারণ, ইমাম ইবনুল আরবীর ভাষায় এ প্রসঙ্গে কুরআন শরীফে বর্ণিত সুস্পষ্ট বিধানের মুকাবিলার অন্য কোনো প্রমাণ অগ্রাহ। কুরআন বলছে : “মৌসুমের ফলমূল থেকে খাও; কিন্তু ফসল সংগ্রহের দিনে ন্যায্য হিস্যা দান করে দাও।” (৬ : ১৪১)
দ্বিতীয় কারণটি হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জীবদ্দশায় এ ব্যবস্থার প্রচলন না থাকলেও আমাদেরকে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হবে যে, তিনি হয়তো বিষয়টি তাঁর উম্মতের বিবেকের ওপর ছেড়ে দিয়েছেন। কেননা সে যুগে ফলমূল ও খাদ্যশস্য সংরক্ষণ করা কষ্টকর ছিলো।
অবশ্য উক্ত পন্ডিত স্বীকার করেছেন যে, একটি হাদীসে কেবল খেজুর, গম, কিসমিস ও বার্লির ওপর যাকাত সীমাবদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু এ হাদীসটিও দুর্বল এবং কোনো কোন হাদিস বিশারত এর প্রামাণিকতা স্বীকার করেননি বিধায় কোনো মাযহাব একে প্রমাণিক বলে গ্রহণ করেনি। সুতরাং সকল ফলসের ওপর যাকাতের বাধ্যতামুলক বিধানকে কিভাবে অস্বীকার করা যায় যখন কুরআন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলছে : “তিনিই লতা ও বৃক্ষ উদ্যানসমূহ সৃষ্টি করেছেন এবং খেজুর বৃক্ষ বিভিন্ন স্বাদ বিশিষ্ট খাদ্য শস্য, জলপাই ও ডালিম র্সষ্টি করেছেন। এগুলো একে অন্যের সদৃশ এবং বিসদৃশও। যখন এটা ফলবান হয় তখন ফল খাবে আর ফসল তুলবার দিনে এর দেয় প্রদান করবে। ” (৬:১৪১)
আরেকটি আয়াতে বলা হয়েছে: “হে ইমানদারগন, তোমরা যা কিছু উপার্জন করো এবং আমি যা ভূমি থেকে তোমাদের জন্য উৎপাদান করে দিই তার মধ্যে যা উৎকৃষ্ট তা ব্যয় করো।” (২:২৬৭)
একটি প্রমানিক হাদীসেও যাকাত প্রদানের বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হিয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, “নদী অথবা বৃষ্টির পানি বিধৌত জমি থেকে এক-দশমাংশ; (সেচের) পানি সিঞ্চিহত জমি থেকে শতকরা পাঁচ ভাগ।” (ইমাম আবু হানিফা: আহকামুল কুরআন)
এই হাদীসে কোনো বিশেষ ফসলের মধ্যে যাকাতকে সীমিত করা হয়নি। এখানে বাধ্যতামূলক হার পরিষ্কারভাবে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। পরবর্তীকালে উমর ইবনে আবদুল আজিজ ও ইমাম আবু হানিফা (রহ) এ ব্যাপারে কুরআনী আয়াতের (৬:১৪১)
ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে ইমাম আবু হানিফা (রহ)-র মতগুলোকে অপেক্ষাকৃত সুদৃঢ় বলে উল্লেখ করেছেন। অনান্য মাযহাবের প্রমাণগুলোকে দুর্বল আখ্যায়িত করে ইবনুল আরবী (রহ) বলেছেন, “ আবু হানিফা (রহ) (পূর্বোউল্লিখিত) মূল সূত্রগুলোকে আয়নার মত ব্যবহার করেসত্যকে অবলকন করেছেন।” শরাহ আত-তিরিমিযীতে আরবী (রহ) বলেন, “(যাকাতের ব্যাপারে) আবু হানিফা (রহ)-এর মাযহাব সূদৃঢ় প্রমাণ পেশ করেছে।” আহকাম ও তাদের কারনগুলোর মধ্যেকার সঙ্গতি উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হলে মারাত্মক স্ববিরোধিতার আশংকা থাকে। তখন আমরা একই বিষয়কে ভাগ ভাগ করে দেখি। আবার বিভিন্ন বিষয়কে এক করে ফেলি। এটা হচ্ছে সুবিচারের পরিপন্থী যার ওপরে আশ-শারীরাহ প্রতিষ্ঠিত পাণ্ডিত্যভিমানীরা কোনো জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি ছাড়াই আহকামের কারন খুঁজতে গিয়ে বিষয়গুলোকে জটিল করে তোলেন। এ জন্যে জনগণের কছে সত্য স্পষ্ট করে তুলে ধরতে আমাদের প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে অথবা বিজ্ঞ ও যোগ্য ব্যক্তিদের জন্যে ইজতিহাদের দ্বার খুলে দিতে হবে। সেই অনধিকার চর্চাকারী পরজীবীদের বিরুদ্ধেও সতর্ক থাকা দরকার।
১. ছোট খাট বিষয় নিয়ে মেতে থাকা
বুদ্ধিবৃত্তিক বন্ধাত্বের একটি লক্ষন হচ্ছে বড় বড় বিষয় উপেক্ষা করে ছোটখাট বিষয় নিয়ে মেত থাকা। অথচ বৃহৎ বিষয়গুলৌ এতো গুরুত্বপূর্ন যে, এগুলোর প্রতি উদিসীন উম্মাহর অস্তিত্ব, আশা-আকাক্ষা, পরিবেশ তথা সামগ্রিক সত্তাকে বিপন্ন করতে পারেঅ দাড়ি রাখা, গোড়ালীর নিচে পযর্ন্ত কাপড় পরা, তাশাহুদের সময় আঙ্গুল নাড়ানো, আলৌকচিত্র রাখার মতো ছোটখাট বিষয়গুলো নিয়ে অবিরাম বাড়াবাড়ি চলছে।এমন এক সময় এসব নিয়ে হৈ চৈ করা হচ্ছে যখন মুসলিম উম্মাহ ধর্ম নিরপেক্ষবাদ, ইহুদীবাদ ও খৃষ্টবাদের নিরবচ্ছিন্ন বৈরিতা ও অনুপ্রবেশের সম্মুখীন। ক্রীশ্চান মিশনরীরা মুসলমানদের ঐতিহাসিক ও ইসলামী চরিত্র ক্ষুণ্ণ করার জন্যে নতুন ক্রুসেড শুরু করেছে। দুনিয়ার বিভিন্ন আংশে মুসলমানদেরকে নির্মমভাবে হত্যা করা হচ্ছে। মুসলিম ধর্ম প্রচারকরা চরম ভীতি ও নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন। আমি দেখছি, যারা শিক্ষাদীক্ষা আথবা জীবিকা অর্জনের জন্যে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও ইউরোপে এসেছেন, তাঁরাও ছোটখাট বিতর্কিত বিষয়গুলো সাথে নিয়ে এসেছেন এবং এ নিয়ে মাথা ঘামান। এটা এক কথায় র্মমান্তিক! আমি নিজে দেখেছি এবং শুনেছি এসব বিষয় নিয়ে উত্তপ্ত বিতর্ক হয়েছে যে, শেষ পর্যন্ত মুসলমানদের মধ্য অনৈক্য ও বিভেদ সৃষ্টি হয়েছে। অথচ বিষয়গুলো ইজতিহাদ সাপেক্ষ। এগুলো এমন বিষয় যা নিয়ে ফকীহদের মত সর্বস্মত হয় না। আমি নিজেও এগুলের ওপর বক্তব্য রেখেছি। যা হোক এসব নিরর্থক মাসলা-মাসাকয়েল নিয়ে ঝগড়া-বিবাদ না করে প্রবাসীদের উচিত ইসলামের মূল সত্যকে আঁকড়ে ধরা। বিশেষ করে মুসলিম তরুণদের এদিকে আকৃষ্ট করা, তাদেরকে অবশ্য পালনীয় কাজগুলো করতে এবং কবীরা গুনাহ থেকে বিরত থাকতে উদ্বুদ্ধ করা। এই দায়িত্ব পালনে সফল হলে ইসলাম প্রচারে এক নতুন আশার সঞ্চার হেব।
এটা দুঃখজনক যে, যারা এ ধরনের বিতর্ক ও সংঘাতের সূত্রপাত করেন তারাই অনেক গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় বিধি পালনে উদাসীন বলে অভিযোগ রয়েছে। মাতা-পিতার প্রতি কতব্য, স্ত্রী ও সন্তান প্রতিপালন, প্রতিবেশির সাথে সদ্ভাব, সঠিকভাবে নিজ দায়িত্ব পালন, বৈধ ও অবৈধ বিচারে সতর্কতা ইত্যাদি প্রশ্নে তাদের বিরুদ্ধে অবহেলার অভিযোগ শোনা যায়। কিন্তু তারা নিজেদের মান উন্নত করার পরিবর্তে বিতর্ক সৃষ্টি করে খুব মজা পান। শেয় পর্যন্ত তাদেরকে এর দরুন বৈরিতা অথবা মুনাফিকীর ন্যায় আচরণ করতে হয়। একটি হাদীসে এরূপ বাক-বিতন্ডার কথা উণ্ণখ করা হয়েছে : “যারা (সঠিক) পথ পেয়েছে তারা কখনো বিভ্রান্ত হবে না যতক্ষন না তারা বাক-বিতন্ডায় নিমজ্জিত হয়।” (আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিযী) এ রকমও দেখা যায়, কেউ কেউ আহলে কিতাবদের জবাই করা পশুর গোশত মুসলমানদেরকে খেতে নিষেধ করেন যদিও বর্তমান ও অতীতে এর বৈধ হওয়া সম্পর্কে ফতোয়া আছে। অথধচ এ রকম লোকদেরই দেখা যাবে এর চেয়ে বড় বড় নিষিদ্ধ কাজ করতে তারা সিদ্ধহস্ত। যুক্তরাষ্ট্রে এ ধরনের একটা ঘটনার কথা আমি শুনেছি। এক ব্যক্তি খুব বড় গলায় বলছিল ইহুদী ও খৃষ্টানদের জবাই করা পশুর গোশত খাওয়া যাবে না। কিন্তু সে নির্লজ্জের মতো অন্যদের সাথে একই টেবিলে বসে মদ সহযোগে ঐ গোশত ভক্ষণ করছিলো। অথচ সে নির্দ্বিধায় একিট অনিশ্চত ও বিতর্কিত বিষয়ে গোঁড়া বক্তব্য রাখছিলো। ঠিক এ রকম পরস্পর বিরোধী আচরণ দেখে একবার হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। হযরত হুসাইনের (রা) শাহাদাতের পর ইরাক থেকে এক ব্যক্তি এসে তাকে মশা মারা হালাল কি হারাম জিজ্ঞেস করলো। ইমাম আহমদ তাঁর মসনদে বর্ণনা করছেন:
আমি ইবনে উমরের সাথে বসেছিলাম। একিট লোক এসে তাকে মশার রক্ত সম্পর্কে জিজ্ঞস করলো। ইবনে উমর (রা) তাকে বললেন, “তুমি কোত্থেকে এসেছ?” সে জবাব দিল, “ইরাক থেকে।” তখন ইবনে উমর বললেন, “দেখ লোকটির দিকে! সে আমাকে মশার রক্ত সম্পর্কে প্রশ্ন করছে, অথচ তারা (ইরাকিরা) রাসূলুল্লাহ (সা)- এর পৌত্রকে [আল-হুসাইন ইবনে আলী (রা)] হত্যা করেছে। আমি রাসূলুল্লাহ (সা) - কে বলতে শুনেছি : “তারা (হাসান ও হুসাইন) এই জগতে আমার দু’টি মিষ্টি মধুর সুরবিত ফুল।” (আহমাদ)
২. নিষেধাজ্ঞা নিয়ে বাড়াবাড়ি
ইসলামী আইনশাস্র ও শরীয়াহর জ্ঞানের অবাবে নিষেধাজ্ঞার ক্ষেত্র নিয়ে অধিক বাড়াবাড়ি দেখা যায়। কুরআন ও সুন্নায় এর বিরুদ্ধে পরিস্কার সতর্ক বাণী রয়েছে। কুরআন বলছে :
“তোমাদের মুখ থেকে যেসব মিথ্যা বের হয়ে আসে তেমনি করে তোমরা আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে বলো না যে, এটি হালাল এবং ওটি হারাম।” (১৬: ১১৬)
রাসূলুল্লাহ (সা) - এর সাহাবী এবং প্রাথমিক যুগোর বুজর্গানে দ্বীন নিশ্চত না হওয়া পর্যন্ত কনো জিনিসকে নিষিদ্ধ বা হারাম বলে ফতোয়া দিতেন না। কিন্তু চরমপন্থীরা তাৎক্ষণিকভাবে হারাম ফতোয়া দিতে যেন এক পায়ে খাড়া থাকে। ইসলামী আইনশাস্ত্রে কোন বিষয়ে যদি দুটো মত থাকে যদি এক পক্ষ বলে মুবাহ, আন্য পক্ষ বলে মাকরূহ; চরমপন্থীরা এক্ষেত্রে মাকরূহকে সমর্থন করে পরহেযগারী যাহির করে। এক পক্ষ যদি একটি বিষয়কে মাকরূহ এবং অন্য পক্ষ হারাম বলে ঘোষণা করে সে ক্ষেত্রে গোঁড়া ব্যক্তিরা হারামের পক্ষ নিয়ে সাধুতার প্রমাণ রাখতে চায় অর্থাৎ সহজ ও কঠিনের মধ্যে তারা শেষোক্তটাকে বেছে নেয়াই অধিকতর তাকওয়ার লক্ষণ বলে মনে করে। তারা ইবনে আব্বাসের (রা) কঠোর মত গ্রহণে বেশি আগ্রহী। বস্তুত এই প্রবণতা মধ্যমপন্থার দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে তাদের অজ্ঞতারই ফসল। বিষয়টি বোঝায় সুবিধার্থে আমি একটি প্রত্যক্ষ ঘটনার উল্লেখ করতে চাই।
একদিন এক গোঁড়া লোক অপর এক ব্যক্তিকে দাঁড়িয়ে পানি পান করতে দেখে তার পাক সাফ হওয়ার
জন্যে তৎক্ষণাৎ বমি করতে বলল। আমি তখন গোঁড়া লোকটিকে নম্রবাবে বললাম, “এজন্য এতো কঠোর ব্যবস্থার দরকার পড়ে না। এটা একটা চোট ব্যাপার।” সে বলল, হাদীসে এটা স্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ। আর কেউ যদি ভুলক্রমে করে বসে তবে সহীহ হাদীসে বমির বিধান আছে।” আমি জবাব দিলাম, “কিন্তু দাঁড়িয়ে পানি খাওয়ার পক্ষে যে হাদীস আছে তা অধিক প্রমাণিত এবং বুখারীর একটি অধ্যায় আছে যার শিরোনাম হলো, “দাড়িয়ে পানি পান করা।” ঐ ব্যক্তি নিষিদ্ধ হওয়ার পক্ষে কোনো হাদীসের উদ্ধৃতি দিতে পারলো না। অথচ এটা সত্য যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বিদায় হজ্জের সময় দাঁড়িয়ে পানি পান করেছিলেন। (বুখারী, মুসলিম)
এছাড়া একবার হযরত আলী (রা) দাঁড়িয়ে পানি পান করতে করতে বলেছিলেন, “এটা অনেকেই পছন্দ করে না, কিন্তু আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে এরূপ করতে দেখেছি যেমন তোমরা আমাকে দেখছ।” (বুখারী, মুসলিম)
ইবনে উমরের (রা) উদ্ধৃতি দিয়ে ইমাম তিরমিযী বলছেন, “রাসূলুল্লাহ (সা)-এর যুগে আমরা চলন্ত অবস্থায় খাবার খেতাম এবং দাঁড়িয়ে পানি পান করতাম।” কাবশাহ (রা) বলেন, “আমি একবার রাসূলুল্লাহ (সা) -কে ঝুলন্ত মশক থেকে পানি পান করতে দেখেছি।”
মোটকথা নির্ভরযোগ্য হাদীস বিশারদদের ব্যাখ্যা থেকে আমরা দেখতে পাই বসে পানি পান করাকে উৎসাহিত করা হয়েছে বটে, কিন্তু দাঁড়িয়ে পান করতে নিষেধ নেই। আর দু’টো ব্যাপারই প্রমাণিত। অতএব, কেউ দাঁড়িয়ে পান করলেও নিষেধ নেই। কেউ দাঁড়িয়ে পানি পান করলেই বমির বিধান জারি করাটা সম্পুর্ণ ভুল।
একইভাবে, আজকাল অনেক তরুণ ইসলামী পোশাক নিয়ে জল্পনা কল্পনায় লিপ্ত। হাদীসে এর দৃঢ় ভিত্তি আছে: “(পোশাকের) যে অংশ গোঁড়ালির নিচে (ঝুলে থাকে) তা আগুনে (পুড়বে)।” (বুখারী)
এ জন্য অনেক তরুণকে গোঁড়ালির উপরে পোশাক পরতে দেখা যায় এবং তাদের সঙ্গী-সাথীদের উপরেও এটা চাপাতে চায়। কিন্তু এরূপ চাপাচাপির ফলটা এই হবে যে, একপক্ষ অপরপক্ষের বিরুদ্ধে নিশ্চিতভাবেই গোঁড়ামির অভিযোগ আনবে। এটা সত্য যে, কিছু হাদীসে গোড়ালির নিচে কাপড় পরিধানের বিরুদ্ধে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। আবার অন্য হাদীসে এই নিষেধাজ্ঞার কারণ খুঁজে পাওয়া যায়। একদা এভাবে কাপড় পরাকে অহঙ্কার, ঔদ্ধত্য ও অপচয়ের লক্ষণ মনে করা হতো। দৃষ্টান্তস্বরুপ রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, “আল্লাহ কিয়ামতের দিনে সেই ব্যক্তির দিকে থাকবেন না যে অহঙ্কারবশত তার কাপড়কে (পেছনে) টেনে নিয়ে যায়।” (মুসলিম)
হযরত আবু বকর (রা) রাসুলুল্লাহ (সা)-কে বললেন, “আমার ইজার অসাবধানতাবশত নিচে নেমে যায়।” রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন “যারা গর্বোদ্ধত হয়ে এরূপ করে তুমি তাদের মধ্যে নও।” (বুখারী) এ কারনে আন-নববী ও অন্যান্য মুসলিম মনীষীরা তম প্রকাশ করেছেন যে, এরূপ কাপড় পরা মাকরূহ। কিন্তু মাকরূহ অনিবার্য কারণে মুবাহ হতে পারে।
৩. ভ্রান্ত ধারণা
ইসলামের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিক সম্পর্কে অগভীর জ্ঞান থেকেই মূলত বিতর্কের সূত্রপাত। এ জন্যে ইসলাম, ঈমান, কুফর, নিফাক ও জাহিলিয়াত ইত্যাদির সঠিক সংজ্ঞা ও পূর্ণ ব্যাখ্যা প্রয়োজন। ভাষাগত জটিলতা, বিশেষত আরবী ভাষায় ব্যুৎপত্তির অভাব বহুলাংশে বিভ্রান্তি ও ভ্রান্ত ধারণার জন্যে দায়ী। ফলত অনেকেই রূপক ও প্রকৃত অর্থের মধ্যে তারতম্য উপলদ্ধি করতে পারেন না। ঈমান ও পূর্ণ ইমান, ইসলাম ও প্রকৃত ইসলাম, বিশ্বাসে মুনাফেকী ও কর্মে মুনাফিকী, ছোট ছোট শিরক ও বড় বড় শিরকের মধ্যে তারা পার্থক্য করতে অক্ষম। এখন আমি এসব বিষয়ের একিট সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিচ্ছি। এতে এ সম্পর্কে আমারা সতর্ক হতে পারব। বস্তুত অনুভূতি, কথা ও কাজের সমন্বয়ে ঈমান পূণৃ রূপ লাভ করে।
কুরআনে এই ঈমান সম্পর্কে বলা হয়েছে :
“মুমিন তো তারাই যাদের হৃদয় কম্পিত হয় যখন আল্লাহকে স্মরণ করা হয় এবং যখন তাঁর আয়াত তাদের নিকট পাঠ করা হয়, তখন তা তাদের ঈমান আরো বৃদ্ধি করে দেয়।” (৮:২)
“সেসব ঈমানদারই সফলকাম হয়েছে যারা বিনয়াবনত চিত্তে নামায আদায় করে।” “তারাই ঈমানদার যারা আল্লাহ ও রাসূলের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং তারপর কখনোই সন্দেহ পোষন করেনি এবং আল্লাহর রাস্তায় জান ও মাল দিয়ে লড়াই করেছে। তারাই সত্যনিষ্ঠ।” (৪৯: ১৫) নিম্মোক্ত হাদীসেও ঈমানের এই রূপ তুলে ধরা হয়েছে:
“যারাই আল্লাহ ও কিয়ামত দিবসের ওপর ঈমান এনেছে তাদের উচিত আত্মীয়-স্বজনের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা ... যা ভাল তাই তাদের বলা উচিত নতুবা চুপ থাকা (উত্তম)।” (বুখারী)
আরেকটি হিদীসে ঈমানের নেতিবাচক দিক তুলে ধরা হয়েছে : “সেই ব্যক্তি ঈমানদার হবে না যতক্ষণ না সে তার (মুসলমান) ভাইয়ের জন্যে তাই ভাল মনে করবে যা সে তার নিজের জন্য ভাল মনে করেব।” (বুখারী)
এখানে লক্ষণীয়, শোষোক্ত হাদীসে দু’টিতে ঈমানের নেতিবাচক রূপ তুলে ধরে প্রকুতপক্ষে ঈমানের পূর্ণ রূপ তুলে ধরা হয়েছে।; সেরূপ ঈমান নয় যেমন বলা হয়: “যে তার জ্ঞান কাজে লাগায় না সে বিদ্বান নয়।” এখানে সীমিত জ্ঞান নয়, বরং পূর্ণ জ্ঞানের নেতিবাচক দিকটির প্রতি ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। এই হাদীসেও পূর্ণ ঈমানের পরিচয় বিধৃত হয়েছে: ঈমানের সত্তরটি শাখা আছে, তার মধ্যে একটি শাখা হচ্ছে লজ্জা বা হায়া। ইমাম আবু বকর আল-বয়হাকী তাঁর ‘আল -জামি’লী শুয়াব আল- ঈমান’ কিতাবে ঈমনকে একটি গাছের সাথে তুলনা করা হয়েছেন। গাছের কান্ড হচ্ছে ঈমানের মৌলিক অঙ্গের প্রতীক। যেহেতু গাছ এর কিছু শাকা-প্রশাখা নিয়ে ইসলামের আওতায় তাকতে পারে। ফেরেশ্তা ও তকদীরের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা।”
আল-হাফিজ আল-বায়হাকী ফতহুল বারীতে লিখেছেন: “আমাদের বুজর্গ পূর্বপুরুষরা বলেছেন : ঈমান হলো হৃদয়ে বিশ্বাস স্থাপন, মুখে উচ্চারণ ও কর্মে রূপায়ণ। এর অর্থ বাস্তব জীবনে রূপায়ণ ছাড়া ঈমান পূর্ণ হতে পরে না। এ জন্যে তারা মনে করতেন ঈমান বাড়াতে ও কমাতে পারে। আল-মাজিয়াহ মনে করেন, ঈমান শুধু মনে ও উচ্চারণে; আল-করামিয়াহ বিশ্বাস করেন, উচ্চারণই যথেষ্ট; আল-মুতাযিলাহর ধারণা, ঈমান হলো বিশ্বাস, উচ্চারন ও বাস্তাবায়নের সমন্বত রূপ।... এ ব্যাপারে তাঁদের ও পূর্ববতী বুজর্গদের মধ্যে পার্থক্য এটাই যে, পূর্বোক্তরা আমলকে ঈমানের প্রমাণ হিসেবে মনে করেন। আর শেষোক্তরা আমলকে পূর্ণতার শর্ত হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু পূর্ণ সত্তা কেবল আল্লাহ তায়ালাই। আমাদের কাছে ঈমানের মৌলিক ঘোষণাই যথেষ্ট। কেননা পরিপূর্ণ পরম সত্তা কেবল আল্লাহ জাল্লা জালালুহু। একবার যে মুখে ঈমানের ঘোষনা দেয় তখন থেকেই আল্লাহ শানুহুর দৃষ্টিতে তাকে মুসলমান হিসেবে গণ্য করা হয। যতোক্ষণ না সে এমন আচরন করে যাতে মনে হয় সে বেঈমান, যেমন মূর্তির কাছে মাথা নত করা। কেউ যখন পাপ কাজ করে তখন তাকে আমরা ঈমন সংক্রান্ত স্ব স্ব ধারণার আলোকে ঈমানদার ভাবতে আবার নাও ভাবতে পারি। পূর্ণ ঈমানদার। কারো বিরুদ্ধে যদি কাফির হওয়ার অভিযোগ ওঠে তবে এ কারণেই যে সে কুফরীর আচরণ করে।’
একজন কাফির যখন এই সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, মুহাম্মদ (সা) তাঁর রাসূল, তখুনি সে মুসলমান হয়ে যায। তৎখণাত সে নামায আদায় করলো কিনা সেটা বড় কথা নয়। যাকাত ইত্যাদি এগুলো সে মেনে নিলো সেটাই বড় কথা। আমল কতটুকু করলো সেটা পরে লক্ষণীয়। কালেমার মৌখিক উচ্চারণের সাথে সাথেই সে জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা পেয়ে গেলো। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, “যারা কালেমা (শাহাদাত) উচ্চারণ করলো, তারা আমার কাছ থেকে জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা পেলো... তাদেরকে আল্লাহর কাছেই জবাবদিহি করতে হবে।” (বুখারী)
ইসলাম শব্দটিও ইবনে উমর (রা) বর্নিত পাঁটি স্তম্ভেকেই বোঝায়: “ইসলাম পাঁচটি স্তম্ভের ওপর প্রতিষ্ঠিত - এই সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই, মুহাম্মদ (সা) তাঁর রাসূল; নামায আদায় করা যাকাত দেয়া, রোজা রাখা এবং হজ্জ আদায় করা।” হাদীস শাস্ত্রেও জিবরাঈল (আ)-এর মুখে ইসলামের সংঙা দেয়া হয়েছৈ। রাসূলুল্লাহ (সা) যখন তাঁকে বলেন, “ইসলাম কী?” তখন তিনি বলেন, “আল্লাহর ইবাদত করা এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক না করা, নামায আদায় করা যাকাত দেয়া এবং রমযান মাসে রোজা রাখা।” (বুখারী)
জিবরাঈল (আ) এর কথা থেকে আমরা ঈমান ও ইসলামের পার্থক্য বুঝতে পারি। এটাও পিরষ্কার যে, দু’টি শব্দকে এক অর্থেও ব্যবহার করা যায়। দু’টির একত্র সমাহারে দেখা যাবে একটির মধ্যে আরেকটির অর্থ লুক্কায়িত আছে, অথাৎ ঈমান ছাড়া ইসলাম নেই। ইসলাম ছাড়া ঈমান নেই। ঈমনের স্থান হৃদয় কন্দরে আর ইসলামের রূপায়ণ হচ্ছে আবেগ ও আচরণের সংমিশ্রণে। নিম্মোক্ত হাদীস থেকে আমরা এটাই উপলব্ধি করতে পারি: “ইসলাম হচ্ছে প্রকাশ্য আর ঈমান হচ্ছে অন্তরে (বিশ্বাসের বিষর)।”(আহমদ, আলবাজ্জাজ)
ঈমানের এই সংজ্ঞা আমরা কুরআনেও দেখতে পাই : “বেদুঈনরা বলে, ‘আমরা ঈমান আনলাম; বল, তোমরা ঈমান আননি বরং, তোমরা বল, আমরা আত্মসমর্পণ করেছি, কেননা তোমাদের হৃদয়ে এখনও ঈমান প্রবেশ করেনি।” (৪৯:১৪)
আর ইসলামের পূর্ণ পরিচয় দিয়ে হাদীসে বলা হয়েছে: “ইসলাম হলো (সেই অবস্থা) যখন তোমার হৃদয় (সম্পূর্ণরূপে) আল্লাহ্ র কাছে সমর্পিত হয় এবং যখন তুমি মুসলমানদেরকে তোমার যবান ও হাত দিয়ে ক্ষতি করা থেকে বিরত থাকো।” অন্য দু’টি হাদীসেও বলা হয়েছে: “সেই হচ্ছে মুসলমান যার যবান ও হাত দিয়ে অন্য মুসলমানের ক্ষতি হয় না” এবং তুমি নিজের জন্য যা ইচ্ছে করো অপরের জন্যে তাই করলেই তুমি মুসলমান।”
ফিকাহর ভাষায় কুফরের অর্থ হচ্ছে আল্লাহ ও তাঁর কালামের প্রতি অকৃতজ্ঞতা ও অস্বীকৃতি। আল-কুরআনে এর প্রতিধ্বনি শোনা যায়: “কেউ আল্লাহ্, তাঁর ফেরেশতা, তাঁর কিতাব, তাঁর রাসূল এবং কিয়ামত দিবমকে অস্বীকার করলে সে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে।” (৪:১৩৬)
কুফর রিদ্দাকেও বোঝায় ফলশ্রুতিতে ঈমান সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়: “কেউ ঈমান ত্যাগ করলে তার আমল নিষ্ফল হবে এবং সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে অর্ন্তভুক্ত হবে।” (৫:৫)
“তোমাদের মধ্যে কেউ যখন দ্বীন থকে ফিরে যায় এবং বেঈমান হয়ে মরে যায়, ইহকালে ও পরকালে তাদের আমল নিষ্ফল হয়ে যাবে। তারাই দোযখী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে।” (২:২১৭) কুফরের অর্থ সীমালংঘনও হয় যা পুরোপুরি ইসলামকে প্রত্যেখানের শামিল নয়, কিংবা আল্লাহ্-রাসূলের অস্বীকৃতিও বোঝায় না।
মনষী ইবনুল কাইয়েম কুফরকে ছোট ও বড় এই দু’ভাগে বিভক্ত করেছেন। বড় কুফরের শাস্তি স্থায়ী জাহান্নাম আর ছোট কুফরের শাস্তি জাহান্নমের অস্থায়ী বাস। একটি হাদীস লক্ষণীয় : “আমার উম্মাহর মধ্যে কুফরীর দু’টি (লক্ষণ) প্রচলিত আছে: “বংশ পরিচয় কলংকিত করা এবং মৃত্যে জন্য বিলাপ” এবং কেউ যদি গণকের খৌঁজ করে এবং তাকে বিশ্বাস করে তবে সে মুহাম্মদ (সা)-এর অবতীর্ণ ওহীর সাথে কুফরী করে।” হাদীসে আরো বলা হয়েছে: “(আমার পরে) পরস্পরকে হত্যা করে কুফরীর দিকে ফিরে যেয়ো না।” কুরআনের একটি আয়াতের এটা হচ্ছে ইবনে উমর (রা) ও অনান্য বিশিষ্ট সাহাবীর ব্যাখ্যা, আয়াতটি হচ্ছে: “আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তদনুসারে যারা বিধান দেয় না তারাই অবিশ্বাসী।” (৫:৪৪) আয়তটির বিভিন্ন ব্যাখ্যা আছে। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন: “এটা সেই কুফরী নয় যা একজনকে ইসলাম থেকে বহিষ্কৃত করে, বরং এটি হচ্ছে কুফরীর একটি উপাদান; কারণ যে ব্যক্তি এরূপ করে সে আল্লাহ ও কিয়ামত দিবসে অবিশ্বাস করে না।” তাউস একই অভিমত প্রকাশ করেছেন। আতা বলেন, এটা হচ্ছে কুফর অথবা অন্যায় অথবা ফিস্ ক যা অপরটির চেয়ে ছোট অথবা বড় হতে পারে। ইকরামার মতো অন্যরা যুক্তি দেখিয়েছেন: আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন সে অনুযায়ী যারা বিচার করে না তারা কুফরী করে। কিন্তু এই যুক্তিটা দুর্বল। কারণ এক ব্যক্তি শরীয়াহর আলোকে বিচার করুক আর নাই করুক, নিরেট অস্বীকৃতিই কুফর। এ প্রসঙ্গে ইবনুল কাইয়েম বলেন: আল্লাহ্র বিধানের পরিপন্থী বিচার বিবেচনার মধ্যে ছোট ও বড় দুই ধরনের কুফরী হয়ে থাকে। আর এটা নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গির ওপর। যদি সে বিশ্বাস করে যে, বিচার আল্লাহ্র বিধান অনুযায়ীই হতে হবে এবং শাস্তির সিদ্ধান্ত নিলো কিন্তু তা করা থেকে বিরত খাকলো তাহলে সে ছোট কুফরী করে। কিন্তু যদি কোন বিশ্বাসী মনে করে যে, এটা বাধ্যতামূলক নয় এবং ঈমানের পরিপন্থী যা খুশী তাই করতে পারে তাহলে সে বড় পাপ করে। কিন্তু যদি সে অজ্ঞতা ও অনিচ্ছাবশত ভুল করে বসে তবে তাকে কেবল “ভুল করেছে” এতটুকু বলা যাবে।
যা হোক বিষয়টির সারাংশ হচ্ছে, সকল সীমালংঘন ছোট কুফরের লক্ষণ, এই অর্থে অকৃতজ্ঞতা; কারণ মান্য করা বা আনুগত্যের মধ্যেই কৃতজ্ঞতার প্রকাশ। অতএব মানবীয় প্রচেষ্টা কৃতজ্ঞতা অথবা কুফর কিংবা এ দুয়ের মাঝখানে কোনো কিছু দিয়ে প্রকাশ পায়-প্রকৃত সত্য আল্লাহ্ পাকই জানেন।
শিরকও দু’ভাগে বিভক্ত: ছোট ও বড়। বড় শিরক হলো আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো উপাসনা করা অথবা তাঁর সাথে অন্য কাউকে শিরক করা। আল-কুরআনের একটি আয়াতে এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে: “আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরীক করলে তিনি মাফ করেন না। তিনি ক্ষমা করেন এর নিম্ন পর্যায়ের পাপ যাকে ইচ্ছা করেন।” (৪:৪৮)
ছোট শিরক হচ্ছে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে শপথ করা অথবা দুর্ভাগ্য সৌভাগ্য পরিণত করার জন্যে তাবিজ-তুমারের ক্ষমতায় বিশ্বাস করা। এই শিরক সম্পর্কে এক হাদীসে বলা হয়েছে, “যে আল্লাহ্ ছাড়া অপর কারো নামে শপথ করে সে শীরক করে এবং যে তাবিজ পরে সে শিরক করে।” (আহমাদ, আলহাকিম) এছাড়া “যাদু, তাবিজ ও ম্যাসকট (কোনো কিছু কে সৌভাগ্যের প্রতীক বলে মানা) বিশ্বাস হচ্ছে শিরক।” (ইবনে হাবান, আলহাকিম)
নিফাকও (মুনাফিকী) ছোট ও বড়-দু’ভাগে বিভক্ত। বড় মুনাফিকী হলো হৃদয়ে কুফরী পোষণ আর বাইরে প্রতারণার উদ্দেশ্যে ঈমানের ভাব করা। এ প্রসঙ্গে কুরআনে বলা হয়েছে: “মানুষের মধ্যে এমন লোক রয়েছে যারা বলে, আমরা আল্লাহ ও কিয়ামত দিবসে বিশ্বাস করি, কিন্তু তারা বিশ্বসী নয়।আল্লাহ্ ও ঈমানদারদের তারা ভাঁওতা দিতে চায়। তারা নিজেদের ছাড়া কাউকে প্রতারিত করে না এটা তারা বুঝতে পারে না।”(২:১৪)
এ ধরনের নিফাকের কথা সূরা আল-মুনাফিকুনে এবং কুরআনের অনান্য আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। এই নিফাকের জন্যে আল্লাহ জাহান্নামের শাস্তির ওয়াদা করেছেন।
“মুনাফিকরা তো দোযখের নিকৃষ্টতম স্তরে থাকবে এবং তাদের জন্যে তুমি কখনো কোনো সহায় পাবে না।” (৪:১৪৫)
ছোট নিফাকের লক্ষণ হচ্ছে আল্লাহ্ ও পরকালের প্রকৃতই বিশ্বাস আছে কিন্তু মুনাফিকের বৈশিষ্ট্যও আছে। ও ব্যাপারে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হাদীস হচ্ছে:
“মুনাফিকীর তিনটি লক্ষণ: সে যখন কথা বলে, (সর্বদা) মিথ্যা বলে; যখন সে প্রতিজ্ঞা করে (সর্বদা) ভঙ্গ করে; যদি তাকে বিশ্বাস করা হয় তবে (সর্বদা) সে অসাধু বলে প্রমাণিত হবে।” (অনুমোদিত হাদীস)
“যার মধ্যে (৪টি বৈশিষ্ট্য) আছে যে নির্ভেজাল মুনাফিক, যার মধ্যে একটি বৈশিষ্ট্য আছে তার মধ্যে নিকাফের একটি উপাদান আছে যতক্ষণ না সে একটি উপাদান আছে যতক্ষণ না সে এটা পরিত্যাগ করে: যখন সে কথা বলে, মিথ্যা বলে; বিশ্বাস করা হলে বিশ্বাসঘাতকতা করে; চুক্তি করা হলে খেলাফ করে এবং যদি সে ঝগড়া করে তবে খুব হঠকারী, অশালীন ও অপমানজনক আচরণ করে।”( অনুমোদিত হাদীস)
রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাহাবাগণ ও বুজুর্গানে দ্বীন এ ধরনের নিফাককে সবচেয়ে বেশি ভয় করতেন। তাঁরা বলতেন, এ ধরনের নিফাক নিফাক নিয়ে কেবল মুনাফিক ছাড়া আর কেউ নিশ্চিত বোধ করবে না, প্রকৃত ঈমানদারই কেবল যার ভয় করে।
৪. রূপকের ওপর গুরুত্ব প্রদান
বর্তমান ও অতীতে অনেক গোঁড়ামি ও ভুল বোঝাবুঝির মূল কারণ হলো স্পষ্ট ভাষণের প্রতি উপেক্ষা করে রূপক অর্থের ওপর বেশি গুরুত্ব দেয়া। রূপক আয়াত হচ্ছে যেগুলোর গূঢ় অর্থ আছে। আক্ষরিক অর্থই শেষ কথা নয়। আর সুস্পষ্ট আয়াত হচ্ছে পরিষ্কার স্বচ্ছ দ্ব্যর্থহীন যার অর্থ বুঝতে বেগ পেতে হয় না। কুরআনুল করীম বলছে: “তিনিই তোমার কাছে এই কিতাব পাঠিয়েছেন, যার কতক আয়াত সুস্পষ্ট দ্ব্যর্থহীন; এগুলো কিতাবের মূল অংশ আর অন্যগুলো রূপক। যাদের অন্তরে সত্য লংঘন প্রবণতা রয়েছে শুধু তারাই ফিত্ না এবং ভুল ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে যা রূপক তার অনুসরণ করে। আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেউ এর ব্যাখ্যা জানেন না।” (৩:৭)
প্রচীন বিদাতী ও গোঁড়া লোকেরা এই রূপক আয়াতগুলোকে চূরান্ত প্রমাণ বলে মনে করেছে। তারা স্পষ্ট মৌলিক বক্তব্যগুলোকে উপেক্ষা করেছে। বর্তমান চরমপন্থীরাও তাই করেছে। বিভিন্ন বিষয়ে তারা এর আলোকে সিদ্ধান্ত নিয়ে ভাল-মন্দ, শত্রু-মিত্র ও কাফির-ঈমানদার নির্ধারণ করেছে। ফলে এক মারাত্মক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। সতর্ক পর্যালোচনা ও পরীক্ষা- নিরীক্ষা ছাড়া কেবল রূপক আয়াতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেয়া জ্ঞানে অগভীরতা ছাড়া আর কিছু নয়। আল-খাওয়ারিজ এভাবে আত-তাকফিরের ফাঁদে পড়েছিলো। তারা তো সকাল মুসলমানকে কাফির বলে মনে করতো কেবল নিজেরা ছাড়া। ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়েই তারা হযরত আলীর (রা) বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল, অথচ তারা তাঁরই সহচর ও সৈনিক ছিলো। তাদের মত পাথর্ক্যের মূল কারণ ছিল আমীর মুয়াবিয়ার সাথে হযরত আলীর (রা) আপোস রফা। হযরত আলী (রা) সৈন্যদের সঙহতি ও মুসলমানদের জীবন রক্ষার জন্যে এ ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। কিন্তু আল-খাওয়ারিজ কুরআনের আয়াতের ভুল ব্যাখ্যা দিয়েআপোস অগ্রাহ করে। আয়াতটি হচ্ছে... “আল্লাহ ছাড়া কারো আদেশ দেয়ার ক্ষমতা নেই।” (১২:৪০০)
আলী (রা) তাঁর সেই বিখ্যাত উক্তি দিয়ে জবাব দিলেন, “একটি সত্য বাণী বাতিলের জন্যে ব্যবহৃত।” বস্তুত সকল আদেশ ও কর্তৃত্ব কেবল আল্লাহ্ র জন্যে- এর অর্থ এই নয়- মানুষ ছোটখাট ব্যপারে শরীয়াহর কাঠামোয় থেকে সিদ্ধান্ত নিতে পারবে না। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) আল-খাওয়ারিজের যুক্তি খন্ডন করেছেন। আপোস - সমঝোতা ইত্যাদি অনুমোদন করে কুরআনে যেসব আয়াত রয়েছে তিনি সেগুলোর উল্লেখ করেছেন। উদাহরণস্বরূপ স্বামী-স্ত্রীর সমঝোতা সংক্রান্ত আয়াতে বলা হয়েছে: “তাদের উভয়ের মধ্যে বিরোধ আশংকা করলে তোমরা তার পরিবার থেকে একজন ও স্ত্রীর পরিবার থেকে একজন সালিশ নিয়োগ করবে; তারা উভয়ে নিষ্পত্তি চাইলে আল্লাহ তাদের মধ্যে মীমাংসার অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করবেন।” (৪:৩৫)
কোনো হজ্জযাত্রী হজ্জের পোশাকে শিকার করলে সালিশরা তার ব্যাপারেও মীমাংসা করে দিতে পারে এমন দৃষ্টান্তও রয়েছে। কুরআন বলছে:
“হে মানদারগণ! ইহরামে থাকাকালে তোমরা শিকার জন্তু বধ করো না; তোমাদের মধ্যে কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে তা বধ করলে তার বিনিময় হলো অনুরূপ গৃহপালিত জন্তু যার ফয়সালা করবে তোমাদের মধ্যে দু’জন ন্যায়বান লোক-বিনিময়ের জন্তুটি কা’বায় পাঠাতে হবে কুরবানীরূপে অথবা তার কাফফারা হবে দরিদ্রকে খাওয়ানো কিংবা সমসংখ্যক সিয়াম পালন করা যাতে সে আপন কৃতকর্মের ফল ভোগ করতে পারে।” (৫:৯৫)
অতএব কুরআন ও সুন্নাহকে গভীরভাবে ও সতর্কতার সাথে অনুধাবন না করলে বিপথগামী হওয়ার আশংকাই সমধিক। বাড়াবাড়ি ও অগভীর জ্ঞানের ফাঁদে পড়ে আজকাল এক শ্রেণীর লোক খারিজীদের মতে শরীয়াহর তাৎপর্য সঠিকভাবে বোধগম্য না হওয়ার দুণই এরূপ গোঁড়ামির উদ্ভব হয়ে থাকে। অন্যদিকে গভীর জ্ঞানের অধিকারী লোক কখনোই হঠকরী আচরণ করতে পারে না। কুরআন-হাদীস সঠিক প্রেক্ষাপটে অধ্যয়ন করলে এর সুসংলগ্ন ও সুমহান অর্থ অনুবাধন করা অসম্ভব নয়। আর এর বিপরীত পন্থায় কুরআন পাঠের অর্থ হবে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ভাষায় তাদের মতো “যারা কুরআন তিলাওয়াত করে কিন্তু অর্থ তাদের হৃদয়ে স্পর্শ করে না।”
সম্ভবত এর মানে এই দাঁড়ায়- আল্লাহ ভাল জানেন- তাদের মৌখিক তিলাওয়াত শারীরিক কসরতের মতো যা কখনো হৃদয়কে প্রভাবিত করে না। এই কথাটি পূর্বে উদ্ধৃত “জ্ঞান ছিনিয়ে নেয়া” সংক্রন্ত হাদীসটির কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।
এ সংক্রান্ত ব্যাখ্যার সাথে হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর ব্যক্তব্যের সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয়। আবু উবায়েদের ফাযায়েলে কুরআন ও ইবরাহীম আত-তায়িমীর বর্ণনার ভিত্তিতে সাঈদ আবনে মনসুরের ব্যাখ্যায় এর উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি বলেন: “একদা একাকী বসে থাকার সময় উমর ইবনে খাত্তাব (রা) বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন, যারা এক রাসূলের অনুসরণ করে এবং কিবলার দিকে মুখ করে নামায পড়ে তারা কেন মতভেদে লিপ্ত হয়। উমর (রা) তখন ইবনে আব্বাস (রা)-কে গিয়ে জিজ্ঞেস করেন, “এই উম্মাহ কেন মতভেদে লিপ্ত হয় যখন তারা এক রাসূল (সা) ও এক কিবলাহ্র অনুসারী?” (সাঈদ-এর সাথে “এবং একই কিতাব” কথাটি যোগ করেছেন)। ইবনে আব্বাস (রা) জবাব দিলেন: “আল-কুরআন নাযিল হয়েছে এবং আমরা তা পাঠ করে ঐশী বাণীর মর্ম উপলব্ধি করেছি। কিন্তু এমন লোক আসবে যারা কুরাআন তিলাওয়াত করবে অথচ এর শানে নুযূল ও বক্তব্য বিষয় উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হবে। ফলে তারা বিভিন্ন রকম ব্যাখ্যা দেবে এবং মতানৈক্যে জড়িয়ে পড়বে।”
ইবনে আব্বাসের (রা)-এর জবানীতে সাঈদ আরো বলেন, “প্রতিটি গ্রুপের একটি মত থাকবে, তারপর মতবেদ থেকে সংঘাত সৃষ্টি হবে।” কিন্তু সেখানে উপস্থিত উমর ও আলী (রা) তাঁর এই অশুভ ব্যাখ্যা পছন্দ করলেন না এবং তাকে ভৎসনা করলেন। কিন্তু ইবনে আব্বাস (রা) চলে যাওয়া মাত্র তার মনে হলো যে, তার কথায় কিছু সত্য থাকতে পারে। তিনি তাকে ডেকে পাঠালেন এবং তার কথার পুনরাবৃত্তি করতে বললেন, সতর্ক বিবেচনার পর উমর (রা) ইবনে আব্বাস (রা)-এর সাথে একমত হলেন।
আশ-শাতিবী লিখেছেন: ইবনে আব্বাস (রা) সঠিক ছিলেন। যখন এক ব্যক্তি একটি সূরা নাযিলের কারণ জানে তখন সে এটাও বুঝতে পারে যে, এর ব্যাখ্যা ও উদ্দেশ্য কী। কিন্তু এ সম্পর্কে অজ্ঞতার ফলে তারা ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে মতভেদে লিপ্ত হয় এবং তাদের মতামতের পেছনে শারীয়াহর কোনো সমর্থন না থাকায় তারা বিভ্রান্ত হয়। এর একটি নযীর পাওয়া যায় ইবনে ওয়াহাবের বর্ণনায়: বাকির জিজ্ঞেস করলেন নাফিকে, “ইবনে উমর (রা) আল-হারুরিয়াদের সম্পর্কে কি চিন্তা করেন? (আল-খাওয়ারিজিকে আল-হারুরিয়াও বলা হয়। কারণ তারা হারাওয়া নামক একটি স্থানে দেখতে পান)। জবাব দিলেন, “ তিনি তাদেরকে খুব খারাপ লোক বলে মনে করেন। কুফফার সংক্রান্ত আয়াত তারা ঈমানদারদের ওপর প্রযোজ্য করে।” সাঈদ এই বক্তব্যের ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছেন, আল-খাওয়ারিজ যেসব রূপক আয়াতের অপব্যাখ্যা দেয় তাদের মধ্যে রয়েছে: “আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুসারে যারা বিধান দেয় না তারাই সত্য প্রত্যাখ্যানকারী।” (৫:৪৪) এর সাথে তারা জুড়ে দেয় এই আয়াতটি, তথাপি কাফেররা স্বীয় পালনকর্তার সংগে অন্যকে সমতুল্য করে। (৬:১)
সুতরাং তারা এই উপসংহার টানে যে, কোনো শাসক যদি ন্যায়পরায়ণতার সাথে শাসন না করে সে কুফরী করে। আর যে কুফরী করলো সে অন্যকে আল্লাহর সাথে শরীক করলো। অতএব সে শিরক করলো। আর এই ভুল বিচারের ভিত্তিতে তারা অন্যকে মুশরিকুন বলে ঘোষণা করে, তাদের সাথে যুদ্ধ করে এবং হত্যা করে। আবনে আব্বাস (রা) এই ধরনের অপব্যাখ্যা ও ভ্রান্ত ধারণার বারুদ্ধে হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেছিলেন। আর এর উৎপত্তি হয় ওহীর অর্থ বুঝতে অক্ষমতার দারুন।
নাফি বলেন, যখনি ইবনে উমর (রা)-কে আল-হারুরিয়াদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হতো তিনি বলতেন: “তারা মুসলমানদেরকে কুফফার ঘোষণা করে, তাদের রক্তপাত ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্তির অনুমোদন কের; তারা নারীর ইদ্দাহর সময় তাকে বিয়ে করে এবং স্বামীর বর্তমানে বিবাহিত মেয়েদের বিয়ে করে। আমি জানি না তাদের চেয়ে আর কে আছে যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যায়।” (শাতিবী, আলইতিসাম)
৫. বিশেষ জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা
চরমপন্থীদের জ্ঞানের অগভীরতার আরেকটি লক্ষণ হচ্ছে তারা ভিন্ন মতাবলম্বীর কথা শুনতে মোটেও রাজী থাকে না কিংবা কোনোরকম আলোচনায় বসতে চায় না। তাদের অর্থাৎ গোঁড়াদের মত যে অন্যের মতের আলোকে বিশ্লেষণ করে গ্রহণ বা বর্জন করা যেতে পারে তাও তারা স্বীকার করে না। তারা বিশেষজ্ঞ আলিমদের কাছ থেকে কোনো শিক্ষা পায়নি। বই-পুস্তক, সংবাদপত্র ইত্যাদি হচ্ছে তাদের স্বল্প জ্ঞানের একমাত্র উৎস। এগুলো আলোচনা পর্যালোচনার সুযোগও পায় না। ফলে তারা যা পড়ে তা থেকে ইচ্ছামতো সিদ্ধান্তে পৌঁছে। সুতরাং তাদের পড়া ও সিদ্ধান্তে যে ভুল হবে তাতে আর সন্দেহ কী! কেউ কোথাও কখনো তাদের মতো যুক্তিপূর্ণ সমালোচনা করলেও এগুলোর প্রতি কেউ তাদে দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। আশ-শারূয়াহ বুঝতে হলে যে নির্ভরযোগ্য আলিমদের শরণাপন্ন হওয়া উচিত সে প্রয়োজনীয়তাও তারা স্বীকার করে না।কোনো মুসলিম তরুণ যদি একা একা এরূপ প্রচেষ্টা চালায় তবে তা হবে আনাড়ি সাঁতারুর মতো গভীর পানিতে ঝাঁপ দেয়া।বিশেষজ্ঞদের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছাড়া শারীয়াহর জ্ঞান পূর্ণ হতে পারে না, বিশেষ করে সেসব ক্ষেত্রে যেগুলো নিয়ে মতভেদ আছে। এ কারণে আমাদের অভিজ্ঞ আলিমরা তাদের কাছ থেকে জ্ঞান আহরণের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেছেন যারা বিষয়বস্তু উপলব্ধি ছাড়াই কেবল কুরআনের হাফিজ হয়েছেন কিংবা কিছু বইপত্র পাঠ করে যাদের অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্কর হয়েছে।
এক শ্রেণীর এই তরুণদের বিভ্রান্তির জন্যে পেশাদার আলিম ও পন্ডিতরা বহুলাংশে দায়ী। তারা মনে করে এই আলিমরা শাসকগোষ্ঠীর সাথে হাত মিলিয়েছে। তাই তারা শাসকদের নির্যাতন, নিপীড়ন ও শরীয়ত বিরোধী কার্যকলাপের বিরোধীতা করার সাহস হারিয়ে ফেলেছে, বরং তারা মুনাফিকের মতো শাসকদের গর্হিত কাজের প্রশংসা ও সমর্থন করে। অথচ বাতিলকে সমর্থন না করে অন্তত তাদের নিশ্চুপ থাকাই নিরাপদ ছিল। সুতরাং তরুণরা বর্তমান এরূপ আলিমদের পরিবর্তে অতীতের আলিমদের অধিকতর নির্ভরযোগ্য মনে করলে অবাক হবার কিছু নেই। একাবর আমি তাদেরকে এ ব্যপারে জিজ্ঞেস করলে তারা পরিষ্কার বলেছে, “নির্ভরযোগ্য আলিম আমরা পাব কোথায়? যারা আছে তারা তো শাসকদের ক্রীড়নক। তাদের মর্জি-মাফিক ফতোয়াবাজীতে ব্যস্ত। শাসক যখন সমাজতন্ত্রী হয়, আলিমদের দৃষ্টিতে তাই ইসলামী; শাসক যদি হয় পুঁজিবাদী, পুঁজিবাদও তখন হয় ইসলামী! তাঁরা ফতোয়া দেন শত্রুর সাথে সন্ধি হারাম; কিন্তু শাসক যখন যুদ্ধ ঘোষণা করেন তখন তাদের জন্যে দোয়া করেন। “তারা আল্লাহ্ যা নিষিদ্ধ করেছেন তা হালাল করতে পারে।” (৯:৩৭)
এসব আলিম মসজিদ ও গীর্জা এবং মুসলিম পাকিস্তান ও হিন্দু ভারতকে সমান চোখে দেখে। আমি এর জবাব দিয়েছি এভাবে: “ব্যপারটি সাধারণ সত্যে পরিণত করা উচিত নয়। নিশ্চয় এমন আলিমও আছেন যারা বাতিলের নিন্দা করেন, নির্যাতন রুখে দাঁড়ান, একনায়কদের সাথে আপোস করেন না ভয়-ভীতি ও প্রলোভন সত্ত্বেও। এসব আলিমদের অনেককে কারাবরণ করতে হয়েছে। তারা নির্যাতিত হয়েছেন। এমনকি ইসলামের জন্যে শাহাদত বরণ করেছেন।”
সেই তরুণটি এটা স্বীকার করলেও বলল, “নেতৃত্ব ও ফতোয়া দেয়ার ক্ষমতা এখনো ঐ শাসকদের হাতে,
আলিমদের নয়-এরাই হচ্ছে তথাকখিত পথবিচ্যুত আলিম।”
অবশ্য এটা কেউ স্বীকার করতে পারেন না যে, ঐ যুবকটি যা বলেছে তা অনেকাংশে সত্য। নেতৃত্ব-অভিভাবকত্বের দায়িত্বপ্রাপ্ত এসব “প্রখ্যাত” “আলিম” সরকারের বন্ধকী পণ্যে পরিণত হয়েছেন এবং ইচ্ছে মতো ব্যবহৃত হচ্ছেন। এ ধরনের আলিমদের জানা উচিত সত্য সম্পর্কে নীরব থাকা বাতিল সমর্থনের শামিল। দুটোই শয়তানী কাজ। একবার মিসরীয় টেলিভিশনে “পরিবার পরিকল্পনা” ও “জন্মনিয়ন্ত্রন” অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণকারী একজন সুপরিচিত মুসলিম বুদ্ধিজীবী তো প্রশ্নই করে বসলেন, এই বিতর্কের উদ্দেশ্য কী, বিরোধীতা না সমর্থন-যাতে তিনি নিজের গা বাঁচিয়ে বক্তব্য রাখতে পারেন। বিতর্কের চেয়ারম্যান ঐ পণ্ডিতের প্রশ্ন শুনে আকাশ থেকে পড়লেন। অথচ এর আগের আলিমরা মত প্রকাশে নির্ভীক ছিলেন, কারো পরোয়া করতেন না। আল্লাহ্ এদের ওপর রহম করুন! এদেরই একজন মিসর সরকারের একজন প্রভাবশালী সদস্যকে সম্বোধন করে বলেছিলেন, “যে ব্যক্তি কাজের খোঁজে পা বাড়ায় তার ভিক্ষের হাত বাড়াবার দরকার পড়ে না।” সমসাময়িক আলিম বা পণ্ডিতরা এ থেকে শিক্ষা নিয়ে নিজেদেরকে নিঃসন্দেহে জ্ঞান-সমৃদ্ধ করতে পারেন।
এখন আলিমদের জ্ঞানগরিমা এতোই সঙ্কীর্ণ যে, তরুণ মুসলমানরা তাদের সংস্পর্শে এসে হতাশ হয়ে পড়ে। এ ধরনের একজন আলিম একবার একটি পত্রিকায় লিখলেন, পিতা ও পুত্রের লেনদেনে যেহেতু কোনো সুদের ব্যাপার থাকতে পারে না। কিন্তু পিতা ও পুত্রের তুলনা দিয়ে তিনি যে যুক্তি খাড়া করেছেন তা বিতর্কিত। মোটকথা এসব আলিম বিভিন্ন বিষয়ে সর্বসম্মত প্রামাণিক সূত্র বাদ দিয়ে দুর্বল সনদের হাদীস দিয়ে নিজেদের যুক্তি প্রতিষ্ঠিত করতে চান। এগুলো সাধুতা সত্যতার খেলাফ। মুসলিম তরুণরা স্বভাবতই এসব কাণ্ড কারখানা দেখে হতাশ হয়ে পড়ে। কোনো কোনো আলিম অনেক সময় সস্তা জনপ্রিয়তা অর্জিত হতে পারে এমন কাজও করে বসেন। এগুলো সচেতন তরুণদের নযর এড়াতে পারে না। আরেকটি ঘটনা।একবার মিশর সরকার বিভিন্ন ইসলামী গ্রুপের কার্যক্রম বন্ধ করে দিয়ে তাদের অনেক সদস্যকে বন্দী করেন। একজন সুখ্যাত আলিম প্রকাশ্য জনসভায় ঘোষণা দিলেন, ইসলামী গ্রুপকে আল্লাহ্ পরিত্যাগ করেছেন। তার যুক্তি ছিল, তাঁরা যদি সঠিক পথের অনুসারী হতেন তবে আল্লাহ্র রহমতে তাদেরকে পুলিশ বা সৈন্য কেউই পরাজিত করতে পারতো না। হক ও বাতিলের এরূপ অদ্ভুত বিচার সম্পূর্ণরূপে ইসলাম বিরোধী। ইসলামের দৃষ্টিতে সত্যের সংগ্রামীদের বিজয় লাভে কতকগুলো শর্ত আছে। সেই শর্ত পূরণ না হলে তাদের পরাজিত হওয়া অপ্রত্যাশিত নয়। অন্যদিকে পরিস্থিতির আনুকূল্যে বাতিলের বিজয় অর্জিত হলেও তা চিরস্থায়ী হতে পারে না, কিছুদিন টিকে থাকতে পারে মাত্র। সমকালীন ইতিহাসে এর অনেক জাজ্জল্যমান নযীর আছে। সবচেয়ে বড় কথা, এখন সত্য ও মিথ্যা বা হক বাতিলের দ্বারা জয়-পারজয় নির্ধারিত হয় না। জয়-পরাজয় নির্ধারিত হয় বৃহৎ শক্তিবর্গের হস্তক্ষেপ। আরবদের উপরে ইসরাঈলের ‘বিজয়’-এর একটি অত্যুজ্জ্বল নযীর।
আমরা কি জানি না, আতাতুর্ক ও তার দুষ্টচক্র মুসলমান জনগণ ও আলিমদের কী নির্মমভাবে দমন করেছে? খিলাফতের পাদপীঠ থেকে কিভাবে ইসলাম বিরোধী ধর্মনিরপেক্ষতা জবরদস্তি তুর্কী জনগণের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে! এখন বলুন, এ দু’পক্ষের মধ্যে কারা হক আর কারা বাতিল? সম্পতি একটি মুসলিম দেশে “পরিবার আইন” প্রবর্তনের বিরোধী বহু শ্রদ্ধাভাজন আলিমের উপর নির্যাতন চালানো এবং মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছে। অথচ ঐ পরিবার আইন সম্পূর্ণ ইসলাম বিরোধী। সংশ্লিষ্ট স্বেচ্ছাচারী সরকার সন্ত্রাসী কায়দায় ঐ আইনের বিরোধী জনসাধারণ ও আলিমকে স্তব্ধ করে দেয়। এর অর্থ কি এই যে, সরকারের পদক্ষেপ সঠিক ছিল, আর শাস্তিপ্রপ্ত আলিমরা ভ্রান্ত? আরেকটি মুসলিম দেশে অমুসলিম সংখ্যালঘু সংখ্যাগুরু মুসলমানদের উপর শাসন চালায়। সেখানে সরকার বিরোধী তৎপরতা দমনের জন্যে প্রায় প্রতিদিন হাজার হাজার মুসলমান নর-নারীকে গ্রেফতার করা হয় এবং নিপীড়ন চালানো হয়। তদুপরি যেসব দৃঢ়চেতা মুসলমান যুলুম সহ্য করে টিকে থাকে তাদের উপর হালাকু ও চেঙ্গিস খানের মতো হিংস্র কায়দায় নির্যাতন চালানো হয় আর তাদের সামনে তাদের কন্যা, বোন বা স্ত্রীদের ধর্ষণ করা হয়।
বস্তুত ইতিহাসে তথা ইসলামের ইতিহাসে মুসলমানদের ওপর এমন নির্যাতন, হত্যাযজ্ঞ ও ধ্বংসলীলার বহু নযীর আছে। হুসাইন ইবনে আলী (রা) পরাজিত হয়েছেন এবং ইয়াজিদ ইবনে আমীর মুয়াবিয়া তাঁর পবিত্র দেহকে ক্ষত-বিক্ষত করেছে। পরিণামে বনু উমাইয়া বহুকাল শাসন করেছে; কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বংশধাররা তাদের হাত থেকে নিষ্কৃত পাননি, এমনকি আব্বাসীয়দের শাসনামলেও নয়। এ থেকে কি এটাই প্রমাণিত হয় যে, ইয়াজিদের কার্যকলাপ সঠিক ছিল আর হযরত হুসাইন (রা)-এর অনুসৃত পন্থা বাতিল? হে আল্লাহ, আপনি এদের যুলুমের সাক্ষী, এদের হাত থেকে উম্মাহকে রক্ষা করুন!
আরো ঘটনা আছে। কয়েক বছর পর বিজ্ঞ ও সাহসী সেনাপতি আবদুল্লাহ ইবনে ইউসুফ অনারবী হাজ্জাজ-বিন-ইউসুফের হাতে পরা জিত হয়েছিলেন; পরে হাজ্জাজ আরেকজন মহান মুসলিম সেনাপতি আবদুর রহমান ইবনে আল-আসাস এবং সাঈদ ইবনে জুবায়ের, আশশাবী, মুতরিয়াসহ একদল বিশিষ্ট আলিমকে হত্যা করে। এগুলো ছিল উম্মাহর জন্যে বিরাট ক্ষতি, বিশেষ করে সাঈদ ইবনে জুবায়ের সম্পর্কে ইমাম আহমদ (র) বলেন, তিনি এমন এক সময় নিহত হলেন যখন তাঁর খুব প্রয়োজন ছিল। প্রসঙ্গত একটি ঘটনা উল্লেখ করা যায়: “আল্লাহর কসম! হিংস্র নেকড়ে যদি আমাদের ছিন্নভিন্ন করে তবুও আমরা আমাদের সত্য বিশ্বাস ও তোমাদের মিথ্যাবাদিতা সম্পর্কে সংশয়ী হবো না।” ইবনে জুবায়ের ও তার সঙ্গী-সাথীরা মক্কায় অবরুদ্ধ হয়ে বলেছিলেন: “আল্লাহর শপথ! সৎ মুত্তাকীদের কেউ অবনত করতে পারবে না যদি গোটা পৃথিবীও তাঁদের বিরুদ্ধে দাঁড়ায় আর বিপথগামীরা কখনোই যথার্থ সম্মান পাবে না যদি তাদের কপালে চন্দ্রও উদিত হয়। এসব উক্তি কুরআনে বর্ণিত নবীদের ঘটনাবলীর সাথে সংগতিপূর্ণ। কুরআন বলছে: “তবে কি যখনি কোনো রাসূল এমন কিছু এনেছে যা তোমাদের মনঃপূত নয় তখনই তোমরা অহংকার করেছে আর কতককে অস্বীকার করেছে এবং কতককে হত্যা করেছ!” (২:৮৭) এমন একজন নবীদের মধ্যে ছিলেন হযরত যাকারিয়া (আ) ও তাঁর পুত্র ইয়ারিয়া (আ)। এই নবীদের হত্যা এবং তাদের শত্রুদের সাফল্যকে কী পূর্বোক্তদের ভূমিকাকে মিথ্যা প্রমাণিত করে? আমরা কুরআনুল করীমে আসহাবুল উখদুদের ঘটনাও জানি। তারা ঈমানদারদের জলন্ত অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করে সেই বীভৎস্য দৃশ্য উপভোগ করতো: “এবং অন্য কোনো কারণে নয়, কেবল তারা সর্বশক্তিমান ও সকল প্রশংসার যোগ্য আল্লাহ্ কে বিশ্বাস করতো বলেই (কাফিররা) তাদের সাথে নিষ্ঠুর আচরণ করেছে।” (৮৫:৮)
কুরআন শরীফে বলা হয়েছে, ঈমানদারদের কখনো কখনো বিপদাপদের মধ্য দিয়ে পরীক্ষা করা হয় এবং বেঈমানদেরকে সাময়িক সাফল্য দিয়ে প্রলুব্ধ করা করা হয়। আল্লাহ বলেন: “মানুষ কি মনে করে আমরা ঈমান এনেছি এ কথা বললেই তাদেরকে পরীক্ষা না করে ছেড়ে দেয়া হবে? তাদের পূর্ববর্তীদেরও আমি পরীক্ষা করেছিলাম; আল্লাহ অবশ্যই প্রকাশ করে দেবেন কারা সত্যবাদী ও কারা মিথ্যাবাদী।” (২৯:২-৩)
ওহুদ যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয়ের পর নিম্মোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়: “যদি তোমাদের আঘাত লেগে থাকে তবে অনুরূপ আঘাত তাদেরও তো লেগেছে। মানুষের মধ্যে এই দিনগুলোর আমি পর্যায়ক্রমে আবর্তন ঘটাই, যাতে আল্লাহ মুমিনদেরকে জানতে পারেন এবং তোমাদের মধ্য থেকে কিছু লোককে শহীদ হিসেবে গ্রহণ করতে পারেন।” (৩:১৪০)
আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন, “...আমি তাদেরকে এমনভাবে ক্রমে ক্রমে ধরব, তারা তা বুঝতেও পারবে না।” (৬৮:৪৪)
৬. ইতিহাস, বাস্তবতা ও আল্লাহর সুনান সম্পর্কে সচেতনতার অভাব
ইসলাম সম্পর্কে সঠিক সচেনতার অভাব ছাড়াও বাস্তবতা, জীবন, ইতিহাস এবং আল্লাহ্ র সৃষ্টির রীতি সম্পর্কেও যথার্থ সচেনতার অভাব রয়েছে। এর অভাবে কিছু লোক অসাধ্য সাধন করতে চায়। যা ঘটতে পারে না তারা তাই কল্পনা করে এবং পরিস্থিতি ও ঘটনা প্রবাহের ভুল বিচার করে বসে যা আল্লাহ্ র রীতি ও শরীয়তী চেতনার পরিপন্থী। তারা অসমসাহসিক পদক্ষেপ নেয়, এমনকি জীবনেরও ঝুঁকি নেয়। এর পক্ষে বিপক্ষে কী প্রতিক্রিয়া হতে পারে তারা তা মোটেও বিবেচনা করে না। কারণ তারা মনে করে তাদের লক্ষ্য তো আল্লাহ্ ও তাঁর কালাম সমুন্নত করা। অতএব এসব লোকের পদক্ষেপকে অন্যরা “আত্মঘাতী” বা উম্মাদনাপূর্ণ বলে অভিহিত করলে আশ্চর্যের কিছু নেই।
বস্তুত এই মুসলমানরা যদি মুহুর্তের জন্যেও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সুন্নাহর প্রতি ভ্রুক্ষেপ করতো তাহলে নিশ্চিতভাবে সঠিক পথ-নিদের্শ লাভ করতো। আমরা এখানে স্মরণ করতে পারি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ১৩ বছরের মক্কী জীবন। তিনি শুধু দাওয়াত দিয়ে ক্ষান্ত হননি, ৩৬০টি মূর্তি থাকা সত্ত্বেও কা’বায় নামায ও তাওয়াফ করতে বলেছেন। কেন এরূপ করলেন? তিনি কাফিরদের তুলনায় তাঁর অনুল্লেখযোগ্য শক্তি ও অবস্থানের কথা ভেবে অতি বাস্তব পদক্ষেপ নিয়েছেন। তিনি কখনোই কমান্ডো হামলা চালিয়ে পাথরের মূর্তিগুলো ভেঙ্গে ফেলার চিন্তা করেননি। তাহলে তো আসর উদ্দেশ্যই পণ্ড হয়ে যেতো। ঐ পদক্ষেপে কাফিরদের মন থেকে তো বহু-ইশ্বরবাদের ভুত মুছে ফেলা যেতো না। তিনি সর্বাগ্রে চেয়েছিলেন তাঁর স্বজাতির মনকে মুক্ত করতে-কা’বাকে মূর্তিমুক্ত করতে নয়। এ জন্যে তওহীদেরশিক্ষা দিয়ে প্রথম মুশরিকদের মন পবিত্র করার লক্ষ্যে এমন একদল ঈমানদার তৈরি করেন যারা তাদের লক্ষ্য সম্পর্কে সচেতন এবং কঠোর অধ্যবসা ও পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে তারা বাতিলৈর বিরুদ্ধে হকের লড়াই চালিয়ে যেতে সক্ষম। এসব বিশ্বাসীর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তারা নিরলস নির্বিকার চিত্তে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্যে কাজ করে যায়, বিজয়ের উল্লাসে তারা মাদকতায় বিভোর হয়ে যায় না, আবার পরাজয়ে মুষড়ে পড়ে না। অবশ্য কখনো কখনো তারা কাফিরদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্যে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর অনুমতি প্রার্থনা করেছিল। কিন্তু তিনি এখনো সময় আসেনি বলে তা অগ্রাহ্য করেছিলেন এবং আল্লাহ্ র নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত ধৈর্য ধারনের উপদেশ দিয়েছিলেন। একদিন রাসূলুল্লাহ (সা) আম্মার বিন ইয়াসির (রা) ও তাঁর পিতাকে নিগৃহীত হতে দেখলেন। তিনি তাঁদেরকে সহ্য করার জন্যে উৎসাহিত করলেন এবং তাঁদের জান্নাতের সুসংবাদ দিলেন। স্বাধীনতা ও ধর্মরক্ষার জন্যে আল্লাহ্ র আদেশ না পাওয়া অবধি ঘটনা এভাবে চলতে থাকে। অবশেষে আদেশ এলো। কুরআনের ঘোষণা: “যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হলো তাদেরকে যারা আক্রান্ত হয়েছে। নিশ্চই আল্লাহ্ তাদেরকে সাহায্য করতে সক্ষম; তাদেরকে তাদের ঘরবাড়ি থেকে অন্যায়ভাবে উচ্ছেদ করা হয়েছে শুধু এ কারণে যে, তারা বলে: আমাদের প্রভু হচ্ছেন আল্লাহ্।” (২২:৩৯-৪০)
কিন্তু এই অনুমতি দেয়া হয়েছে কেবল তখনি যখন রাসূলুল্লাহ (সা) ও তাঁর সাহাবীরা নিজেস্ব আবাসভূমি স্থাপন করে নিজেদের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারপরই তাঁদেরকে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হয়েছৈ। তাঁরা এরপর একর পর এক বিজয় অর্জন করেছেন যতক্ষণ না তাঁরা আল্লাহ্ র হুকুমের মক্কা বিজয় করেছেন। এই মক্কা থেকেই তিনি চলে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন কাফিরদের অত্যাচারে।শৈষ পর্যন্ত তিনি মক্কার মূর্তি ধ্বংস করলেন এবং তিলাওয়াত করলেন এই আয়াত, “ বলো সত্র সমাগত এবং মিথ্যা বালুপ্ত হয়েছে। মিথ্যা তো বিলুপ্ত বাধ্য।” (১৭:৮১)
বিস্ময়ের ব্যাপার, জামায়াত আত-তাকফির আল-হিজরা ইতিহাসের এই ধারাকে অস্বীকার করে। এই অবাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে অবশ্য গ্রুপটির প্রতিষ্ঠাতা শেখ শুকরী ও আবদুর রহমান আবু আল-খায়েরের মধ্যে মতপার্থক্যও হয়েছিলো। আবু আল-খায়ের তাঁর “স্মৃতিকথায়” লিখেছেন যে, ইসলামের ইতিহিসের প্রতি শেখ শুকরীর অবস্থা ছিল না। তিনি এটাকে “অপ্রমাণিক ঘটনাবলী” বলে মনে করতেন। এটা ছিলো সাথে মতভেদের চতুর্থ বিষয়। তিনি কেবল কুরআন শরীফে বর্ণীত ঘটনাবলীকেই ইতহাসের উপাদান বলে মনে করতেন। তাই তানি ইসলামী খিলাফতের অধ্যায় পাঠ করা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন।
ধর্মীয় অজুহাতে ইতিহাস সম্পর্কে ও ধরনের সংকীর্ণ ও অযৌক্তিক দৃষ্টিভঙ্গির ফলে তারা ইসলামের ইতিহাসকেও হারাম ঘোষণা করেছিলেন। ইতিবাচক ও নেতিবাচক, জয় ও পরাজয় তথা সকল বিষয় সমন্বিত একটি জাতির ইতিহাস হচ্ছে সমৃদ্ধ খনির মতো যা থেকে সম্পদ আহরণ করে একটি জাতি তার বর্তমান গড়ে তোলে। যে জাতি ইতিহাসকে উপেক্ষা করে তার অবস্থা স্মৃতিভ্রংশ মানুষের সাথে তুলনীয়, যার কোনো মূল বা দিক-দর্শন নেই। কোনো গ্রুপ বা জনগোষ্ঠী কিভাবে এরূপ একটি অস্বাভাবিক শর্তকে টিকে থাকার ভিত্তি হিসেবে নির্ধারণ করতে পারে? তাছাড়া ইতাহাস হচ্ছে এমন একটি আয়না যাতে আল্লাহ্র বিধান প্রতিবিম্বিত হয়েছে। এজন্যে আর কুরআনে গোটা সৃষ্টিলোক সাধারণ ভাবে এবং মানব জীবনে বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। আর এ কারণেই আল কুরআন ইতিহাসের প্রেক্ষিত অনুধাবন এবং এ থেকে শিক্ষা গ্রহণের আহবান জানিয়েছে। এ প্রসঙ্গে কুরআনের বর্ণনা: “তোমাদের পূর্বে বহু জীবন প্রণালী গত হয়েছে, সুতরাং তোমরা দুনিয়া ভ্রমণ করো এবং দেখ মিথ্যাশ্রয়ীদের কি পরিণাম হয়েছে।” (৩:১৩৭)
আল্লাহ্ রীতির বৈশিষ্ট্য হলো স্থায়িত্ব, তার কখনো পরিবর্তন হয় না। আল কুরআন বলছে: “তারা আল্লাহ্ র নামে দৃঢ় অঙ্গীকার করে বলতে যে, তাদের কাছে কোনো সতর্ক বাণী এলে তারা অন্য সকল সম্প্রদায় অপেক্ষা সৎপথের অধিকতর অনুসারী হবে। কিন্তু যখন তাদের কাছে সতর্ক বাণী এলো তখন তা কেবল এদের বিমুখতাই বৃদ্ধি করলো, যমীনের বুকে ঔদ্ধত্য প্রকাশ এবং কূট-ষড়যন্ত্রের কারণে। কূট-ষড়যন্ত্র এর উদ্যোক্তাদেরকেই পরিবেষ্টন করে। তবে কি তারা প্রত্যক্ষ করেছে পূর্ববর্তীদের প্রতি প্রযুক্ত বিধানের? কিন্তু তুমি আল্লাহ্ র বিধানে কখনো কোন পরিবর্তন দেখতে পাবে না এবং আল্লাহর রীতিতে কোন ব্যাতিক্রম দেখবে না। (৩৫: ৪২-৪৩)
আল্লাহর রীতি যেহেতু অপরিবতর্নীয় ও স্থায়ী তাই যারা দুষ্কর্মে লিপ্ত হয় স্থান-কাল ও জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলের প্রতি আচরণে তিনি একই রীতি প্রয়োগ করেন। এই নীতির একটি শিক্ষনীয় দৃষ্টান্ত আমরা দেথেছি ওহুদের যুদ্ধে। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উপদেশ উপেক্ষা করার দরুন তাদেরকে কঠিন মূল্য দিতে হয়েছিলো। কুরআনুল করীমে একথা উল্লিখিত হয়েছৈ: “কী ব্যাপার! যখন তোমাদের ওপর মুসীবত এল তখন তোমরা বললে এটা কোথা থেকে এলো! অথচ তোমরা তো দ্বিগুণ বিপদ ঘটিয়েছিলে। বলো এটা তোমাদের নিজেদেরই নিকট থকে। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে শক্তিশালী। (৩:১৬৫)
আরেকটি আয়াতে যে কারণে মুসলমানদের পরাজয় বরণ করতে হয়েছে তার পরিষ্কার উল্লেখ করা হয়েছে: “আল্লাহ তোমাদের সাথে তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছিলেন যখন তোমরা আল্লাহ্ র অনুমতিক্রমে তাদেরকে বিনাশ করছিলে যে পর্যন্ত না তোমরা সাহস হারালে এবং নির্দেশ সম্বদ্ধে মতভেদ করলে এবং যা তোমরা ভালবাস তা তোমাদেরকর দেখবার পর তোমরা অবাধ্য হলে।” (৩:১৫২)
কিছু বিছিন্ন ঘটনার দরুণ ইতিহাসে অনেক সন্দেহজনক ঘটনা সংযোজিত হয় সত্য, কিন্তু মূল গটনা প্রবাহ সুরক্ষিত থাকে এবং একাধিক প্রামাণিক সূত্রে তা সমর্থিত হয়। আর সন্দেহপূর্ণ ঘটনাগুলো বিজ্ঞ ব্যাক্তি বিশ্লেষণ করতে পারেন। যাতে সত্য নিরূপণ করা যায়।
পক্ষান্তরে আমরা শুধু ইসলামের ইতিহাস নয়, সৃষ্টির পর থেকে মানব ইতিহাসের প্রতি আমাদের দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত করতে চাই। শুধু ঈমানদারদের ইতিহাস নয়, বরং নাস্তিকদের ইতিহাস থেকেও জ্ঞান আহরণ করা যায়। কেননা আল্লাহ্ র রীতিতে কোনো পক্ষপাতিত্ব নেই।তা তো তাওহীদ পন্থী ও পৌত্তলিক উভয়ের ক্ষেত্রেই সমভাবে প্রযোজ্য। বস্তুত জাহিলিয়ার ভ্রান্ত প্রকৃতি অনুধাবন করতে না পারলে আমরা কুরআনুল কারীমকে এবং ইসলামের বদৌলতে আমরা কী কল্যাণ লাভ করেছি তাও উপলব্ধি করতে সক্ষম হবো না। কুরআনে বলা হয়েছে: “...যদিও তারা পূর্বে স্পষ্ট বিভ্রন্তিতে নিমজ্জিত ছিলো।” (৩:১৬৪) এবং “তোমরা অগ্নি গহবরের কিনারে দাঁড়িয়েছিলে, আল্লাহ তা হতে তোমাদেরকে রক্ষা করেছেন।” (৩:১০৩)
উমর ইবনে খাত্তাব (রা)-এর একটি উক্তিতেও এই মর্ম প্রতিফলিত হয়েছে: “জাহিলিয়ার প্রকৃতি অনুধাবনে ব্যর্থতা শুরু হলে একে একে ইসলামের বন্ধনী বিছিন্ন হতে থাকবে।”
সত্য প্রকাশ যদি পুণ্য হয় তাহলে আমি বলবো ইসলামী আন্দোলনের সাথে সংশ্লিষ্ট অনেকেই ইতিহাস সঠিকভাবে অধ্যায়ন ও অনুধাবন করেননি। ইতিহাস পাঠের অর্থ শুধু বিশেষ বিশেষ সময়ের ঘটনাকে জানা নয়, বরং অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে এর মর্ম উপলব্ধি করা, শিক্ষা নেয়া এবং আল্লাহ্ র রীতিগুলো উদ্ভাসিত করা। নিছক পূর্ববর্তী জাতিগুলোর ধ্বংসাবশেষ অবলোকন করলে কোনো ফায়দা হবে না। শুধূ দেখা আর শোনার মাধ্যমে ইতিহাসের মর্ম উপলব্ধি করা যায় না। এ প্রসঙ্গে কুরআন বলছে: “তারা কি দেশে ভ্রমন করেনি? তাহলে তারা জ্ঞান বুদ্ধিসম্পন্ন হৃদয় ও শ্রুতিশক্তিসম্পন্ন কর্ণের অধিকারী হতে পারতো। আসলে চোখ তো অন্ধ নয়, বরং অন্ধ হচ্ছে বক্ষস্থিত হৃদয়।” (২২:৪৬)
ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর পুনরাবৃত্তি ঘটে এবং একটির সাথে অপরটির সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। কারণ এগুলো একই অপরিবর্তনীয় নিয়মে প্রবাহিত হয়। তাই পাম্চাত্য শিখিয়েছে: “ইতিহাসের চাকা ঘোরা” আর আরবারা বলে, “আজবকের রাত কালকের রাতের মতোই।”
আল কুরআনুল করীমে দৃষ্টিভঙ্গি ও আচার-আচরণে সাদৃশ্যের কারণ হিসেবে অভিন্ন চিন্তা ও দৃষ্টির উল্লেখ করা হয়েছে:
“যাদের জ্ঞান নেই তরা বলে, ‘আল্লাহ কেন আমাদের সাথে কথা বলেন না কিংবা কোন নিদর্শন আমাদের কাছে আসে না কেন? এর আগের লোকেরাও এ ধরনের কথা বলতো। তাদের হৃদয় একই রকম। আমি দৃঢ় প্রত্যয়শীলদের জন্য নিদর্শনাবলী স্পষ্টভাবে বিবৃত করেছি।” (২:১১৮)
কুরায়েশ পৌত্তলিকদের সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেছেন: “এভাবে এদের পূর্ববর্তীদের কাছে যখনি কোনো রাসূল (সা) এসেছেন তারা তাঁকে বলেছে, ‘তুমি তো এক যাদুকর, না হয় এক উম্মাদ!’ তারা কি একে অপরকে এই মন্ত্রাণাই দিয়ে এসেছে? বস্তুত তারা এক সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়।” (৫১:৫২-৫৩)
তাহলে দেখা যায়, আল্লাহ্ র নবীর প্রতি আগের ও পরের জাতিসমূহের দৃষ্টিভঙ্গির অভিন্নতা তাদের মধ্যে সমঝোতার ফলশ্রুতি নয়, বরং সাদৃশ্য হলো অন্যায় ও স্বচ্ছাচারী আচরণে। সুতরাং তাদের দৃষ্টভঙ্গি অভিন্ন কারণ হলো স্বেচ্ছাচারিতা।
যারা ইতিহাসের গুরুত্ব এবং আল্লাহর রীতির মর্ম উপলব্ধি করতে সক্ষম কেবল তারাই অতীত জাতিসমূহের ভ্রান্তি থেকে শিক্ষা নিতে পারে। তারাই প্রকৃত সুখী। তারাই যারা এসব ভুলভ্রান্তি থেকে নিজেরা সতর্ক হয় বটে, কিন্তু অন্যের ভাল দিকগুলোকেও উপেক্ষা করে না। জ্ঞানই ঈমানদারের লক্ষ্য তা সে যেখান থেকেই অর্জন করুক না কেনো। কেননা অন্য যে কোন ব্যাক্তির চেয়ে এটা তারই প্রাপ্য।
৭. দু’টি গুরুত্বপূর্ণ
সাধারণ মুসলমান, বিশেষত ইসলামী আন্দোলনের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যাক্তিদেরকে আল্লাহ্র দু’টি রীতি সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। প্রথম: সৃষ্টি ও বিধানের ক্ষেত্রে সুষ্পষ্ট পর্যায়ক্রমিকতা লক্ষণীয়। অথচ আল্লাহ্ পাক আঁখির পলক পড়ার চেয়ে কম সময়ের মধ্যে বেহেশত ও সৃষ্টিতে সক্ষম! “হও আর তা হয়ে যায়।” (২:১১৭)
তিনি তাঁর (হিসেবে) ছয় দিনে এগুলো সৃষ্টি করেছেন অথাৎ পর্যায়ক্রমে যা কেবল তিনিই জানেন। কেননা “দিন” সংক্রন্ত আমাদের ধারনা থেকে তা ভিন্ন। সকল প্রাণীর বিকাশের ক্ষেত্রেও পর্যায়ক্রমিকতা লক্ষণীয়। ধীরে ধীরে এগুলো পূর্ণতা লাভ করে। দাওয়াতী কাজেও এই প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হয়। পৌত্তলিকতা ও কুসংস্কার থেকে মনকে মুক্ত করার জন্যে প্রথমে সেখানে তওহীদের বীজ প্রোথিত করার প্রক্রিয়া শুরু হয়। এভাবে ঈমানের ভিত্তি মজবুত হলে ওয়াজিবাত ও মুহাররামাতের প্রক্রিয়া চালু করা হয়। এরপর সালাত, যাকাত, সিয়াম ইত্যাদি প্রবর্তন করা হয়। এজন্যে আমরা মক্কী ও মাদানী আয়াতের মধ্যে পার্থ্ক্য লক্ষ্য করি।
আয়েশা (রা) শারীয়ার প্রবর্তন এবং কুরআন নাযীলের পর্যায়ক্রম সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন: প্রথমে কুরআনের যেসব আয়াত নাযিল হয়েছে তাতে জান্নাত ও জাহান্নামের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। (পরে) যখন মানুষ ইসলাম গ্রহণ করলো তখন হালাল ও হারামের বিধান নাযীল হলৌ। যদি প্রথমেই “মদ পান করো না” এবং “ব্যভিচার করো না” নাযিল হতো লোকেরা বলতো, ‘আমরা মদপান ও ব্যভিচার কখনোই ছাড়তে পারব না।’ (বুখারী) সুতরাং যারা ইসলামী জীবন ব্যবস্থা তথা ইসলামী রাষ্ট্র প্রতাষ্ঠার সংগ্রামে নিয়োজিত তাদেরকে পরিবেশ, পরিস্থিতি, প্রতিবন্ধকতা, উপায়-উপকরণ ও সামর্থের দিকে লক্ষ্য রেখে পর্যায়ক্রমে দাওয়াতী কাজ চালাতে হবে। এক্ষেত্রে খলীফা উমর ইবনে আবদুল আজীজের দৃষ্টান্ত স্মর্তব্য। তিনি খেলাফায়ে রাশেদীনের আদর্শ জীবন পুনর্গঠন করেছিলেন। কিন্তু পুনর্গঠন প্রক্রিয়া সহজ ছিলো না। তার পুত্র আবদুল মালিক অত্যন্ত নিষ্ঠাবান মুসলমান ছিলেন। তিনি তাঁর পিতাকে একবার বললেন, “হে পিতা, আপনি কেন হত্যা করেন না? আল্লাহ্ শপথ, সত্যের জন্যে আমরা বা আপনার প্রাণ গেলেও আমি পরোয়া করি না।” কিন্তু উমর জবাব দিলেন, “তাড়াহুড়া করো না আমার পুত্র। আল্লাহ্ পাক কুরআনুল কারীমে দু’বার মদ্যপানেরনিন্দা করেছেন এবং তৃতীয়বারে নিষিদ্ধ করেছেন। আমার ভয় হয়, একবারেই সব চাপিয়ে দিলে এক সাথেই তা প্রত্যাখ্যাত হয় কিনা। এতে ফিতনার সৃষ্টি হতে পারে।” (আল মুয়াফাকাত)
দ্বিতীয়: দ্বিতীয় রীতিটি হচ্ছে প্রথমটির পরিপূরক। প্রতিটি জিনিসের পূর্ণতা বা পরিণতি লাভের নির্দিষ্ট মেয়াদ আছে। মূর্ত ও বিমূর্ত উভয় ক্ষেত্রেই এই রীতি প্রযোজ্য। ফসল পাকার আগেই কাটা যায় না। অপরিপক্ক ফলমূল ও শাকসবজি উপকারের পরিবর্তে ক্ষতি করতে পারে। ঠিক তেমনি মহৎ কাজের সুফল অনেক বছর পরেই পরিদৃশ্যমান হয়। পরিণত হতে যতো সময় লাগবে ততোই তা ফলপ্রদ হবে। এক পুরুষের চেষ্টা-সাধনা অন্য পুরুষে ফল দিতে পারে। মক্কা মুকাররমায় প্রথমদিকে কাফিররা আল্লাহর শাস্তির হুশিয়ারীকে অবিবেচকের মতো উপহাস করতো এবং দ্রুত শাস্তি আনার জন্যে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি আহবান জানাতো। কিন্তু তারা এটা জানতো না যে, নির্দিষ্ট সময়েই তা আসবে। বিলম্বও নয়, দ্রুতও নয়।
“তারা তোমাকে শাস্তি ত্বরান্বিত করতে বলে। যদি নির্ধরিত সময় না থাকতো তবে শাস্তি তাদের ওপর আসবে আকস্মিকভাবে, অজ্হতসারে।” (২৯:৫৩)
“তরা তোমাকে শাস্তি ত্বরান্বিত করতে বলে, অথচ আল্লাহ তাঁর প্রতিশ্রুতি কখনো ভঙ্গ করেন না, তোমাদের গণনার হাজার বছরের সামন।” (২২:৪৭)
এই পর্যায়ে আল্লাহ্ তায়ালা মহানবীর (সা)-এর প্রতি বিগত নবীদের মতো অধ্যবসায়ী হওয়ার উপদেশ দিলেন: “অতএব তুমি ধৈর্য ধারণ কর যেমন ধৈর্য ধারণ করেছিলেন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ রাসূলগণ।”(৪৬:৩৫) বিগত নবী-রাসূল ও তাঁদের অনুসারীদের কঠোর সঙগ্রাম ও ত্যাগ তিতিক্ষার বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন:
“তোমরা কি মনে করো তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে, যদিও এখনও তোমাদের কাছে তোমাদের পূর্ববর্তীদের অবস্থা আসেনি! অর্থ কষ্ট ও দুঃখ-ক্লেশ তাদেরকে স্পর্শ করেছিলো এবং তারা ভীত ও কম্পিত হয়েছিলো। এমনকি রাসূল এবং তাঁর ঈমানদার অনুসারীরা বলে উঠেছিলো, আল্লাহ্র সাহায্য কখন আসবে; নিশ্চয় আল্লাহ্র সাহায্য নিকটবর্তী। কিন্তু সেই নির্দিষ্ট সময় কেবল আল্লাহ্রই জানা আছে। এ জন্যে রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর সাহাবীদের ধৈর্য ধারণ করতে বলতেন এবং নিদির্ষ্ট সময়ের পূর্বে বিজয় প্রত্যাশা থেকে বিরত থাকতে উপদেশ দিতেন। একটি ঘটনা থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। একবার খারায ইবনে আল-আর্ত ইসলামের জন্যে তাঁর দুঃখকষ্ট বরণের কথা বলে আর্লাহ্ র সাহায্য প্রার্থনার আবেদন জানালে রাসূলুল্লাহ (সা) এতোই ক্রুদ্ধ হন যে, তাঁর মুখ লাল হয়ে যায়। তিনি বললেন: “তোমাদের আগে একজন বিশ্বাসীকে লোহা দিয়ে এমনভাবে পিষ্ট করা হয়েছে যে, হাড় ছাড়া তার শরীরের গোশ্ত ও শিরা-উপশিরা অবশিষ্ট ছিলো না। আর একজনকে করাত দিয়ে জীবন্ত অবস্থায় দু’ভাগে চিরে ফেলা হয়েছিলো। কিন্তু তাঁরা কেউই ধর্মত্যাগ করেননি। আল্লাহ্র শপথ, তিনি এমনভাবে দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করবেন যে, একজন ভ্রমনকারী সানা থেকে হাদ্রামাউত পর্যন্ত সফরের সময় এক আল্লাহ্ এবং তার ভেড়ার জন্যে নেকড়ে ছাড়া আর কাউকে ভয় করবে না। কিন্তু তোমরা অধৈর্য।” ( বুখারী)
৮. মুসলিম দেশ থেকে ইসলামের নির্বাসন
একজন নিষ্টাবান মুসলমানের কাছে বর্তমানে সবচেয়ে বেদনাদায়ক ব্যাপার হচ্ছে মুসলিম দেশগুলোতে এসলামী শিক্ষা অনুসারণের অভাবে বিকৃতি, দুর্নীতি ও মিথ্যা ব্যাপাকভাবে ছড়িয়ে পড়ছে। মার্ক্সবাদের ও ধর্মনিরপেক্ষতার ছোবলে মুসলিম সমাজ বিপর্যস্ত। আধুনিক “ক্রুসেডাররা” ক্লাব, থিয়েটার, অশ্লীলতা, পর্নোগ্রাফি, ছায়াছবি, নাচ-গান, মদ তথা সর্বক্ষেত্রে মুসলমানদেরকে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করছে। সংবাদপত্রে তারা অনুপ্রবেশের জাল বিস্তার করেছে। রাস্তাঘাটে অর্ধোলঙ্গ নেশাসক্ত নারীদের অবাধে চলাফেরা করতে দেখা যাচ্ছে। আর এসবই হচ্ছে মুসলিম সমাজকে অবক্ষয়ের দিকে ঠেলে দয়ার সুগভীর চক্রান্তের ফল।
এছাড়া মুসলিম দেশগুলোতে এমন সব বিষয়ে আইন প্রণয়ন করা হচ্ছে যা শরীয়তে নিষিদ্ধ অথচ ভাব দেখানো হয় উম্মার বিশ্বাস ও মূল্যবোধ উজ্জীবিত করাই এর লক্ষ্য। কিন্তু মূলত এসব আইনের উৎস শরীয়ত নয়,বরং ধর্মনিরপেক্ষ দর্শন। সুতরাং এতে বিস্ময়ের কিছু নেই- এসব আইন আল্লাহ্ যা নিষিদ্ধ করেছেন তাকে সিদ্ধ করে আর আল্লাহ্ যা সিদ্ধ করেছেন তাকে অসিদ্ধ ঘোষণা করে। আর এসব তথাকথিত আধুনিক আইন সব রকম দুর্নীতি ও অনাচারকে প্রশ্রয় দেয়। অন্যদিকে শাষকদের কার্যকলাপও হতাশাব্যঞ্জক। তারা ইসরামের শত্রুদের সাথে সন্ধি করে আর ইসলামের কথা শোনা যায় নিছক ধর্মীয় উপলক্ষ্য ছাড়া তাও আবার সাধারণ মানুষকে ধোঁধা দেয়ার জন্যে।
মুসলিম দেশগুলোর অর্থনৈতিক অবস্থা ও ব্যবস্থাপনা আরো করুণ। তরুণরা তাদের চোখের সামেন সামেন দেখেত পাচ্ছে ধনী ও দরিদ্রের কী অহসনীয় বৈষম্য! কেউ কোনোভাবে জীবন ধারণ করছে, এমনকি ওষুধপথ্যও সংগ্রহ করতে পারছে না কিংবা মাথা গোঁজারও ঠাঁই নেই। অন্যদিকে বিত্তবানরা লাখ লাখ টাকা মদ ও নারীর পেছনে ঢালছে, বড় বড় প্রাসাদে বাস করছে কিৎবা অনেক সময় খালিই পড়ে থাকে। বিদেশী ব্যাংকে তারা কোটি কোটি ডলার গোপনে সঞ্চয় করছে। তারা তেলের টাকা অপহরণ, পাশ্চাত্যের সাথে সহযোগিতা এবং আর্ন্তজাতিক কোম্পানীগুলোর সাথে লেনদেন করে বিত্তের পাহাড় গড়েছে। আর এই অর্থ তারা জুয়া এ নরীর পেছনে অকাতরে ব্যয় করছে। এর একটি অংশও যদি তারা দরিদ্র মানুষের জন্যে দান করতো তাহলে হাজার হাজার মানুষের অন্ন ও আশ্রয়ের সংস্থান হতো। অথচ এই সুবিধাভোগী শ্রেণী দিনে দুপুরে ডাকাতির মতো জনগণেরন সম্পত্তি অপহরণ করে চলছে। সুদ, ঘুষ, স্বজনপ্রীতি তো আছেই কিন্তু এদের বিরুদ্ধে আইন প্রয়োগ করার কেউ নেই। আইনের হাত থেকে বাঁচার রাস্তাও তাদের জন্য সহজ। সুতরাং এই নিদারুণ পরিস্থিতি সমাজের বিভিন্ন অংশের মধ্যে ঘৃণা-বিদ্বেষ সৃষ্টি করবে, এতে আর সন্দেহ কী! আর এই সুযোগের জন্যে ওৎ পেতে বেস থাকে সর্বনাশা মার্ক্সবাদীরা। তখন তারা বিকল্প হিসেবে শ্রেণী সংগ্রামের কাজ জারি করে দেয়।
এক্ষণে এই মর্মান্তিক অবস্থায় মূল কারণ সর্ম্পকে কোনো হেঁয়লির অবকাশ নেই। একটি পূর্ণাঙ্গ ভারসাম্যময় ও সুবিচারপূর্ণ বিধান হওয়া সত্ত্বেও ইসলাম আজ স্বদেশেই নির্বসিত। সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, রাষ্ট্র পরিচালনা, মানুষ ও সৃষ্টিকর্তার সম্পর্ক তথা সর্বক্ষেত্রে আজ ইসলাম অপসারিত। খ্রীষ্টানদের অবক্ষয়ের সময় যে অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিলো এখন মুসলমানদের অবস্থা তাই। ইসলামকে শরীয়ত ছাড়া দ্বীন, রাষ্ট্র ছাড়া ধর্ম এবং কর্তৃত্ব ছাড়া আইনের কিতাবে পর্যবসিত করা হয়েছে। মুসলমানদেরকে এমন পরিনামের দিকে ঠেলে দেয়া হয়েছে যার সাথে তার নিজস্ব ইতিহাসের কোনো সাদৃশ্য নেই। ক্যাথলিক গীর্জা সব রকম অনাচারে নিমজ্জিত হয়েছিলো। তারা স্বৈরাচারী শাসকদের পৃষ্টপোষকতা করে সাধারণ মানুষের ওপর নিপীড়ন চালিয়েছিলো। সামান্য বিরোধিতা তারা সহ্যকরতে পারতো না। স্বাধীনভাবে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা ছিলো নিষিদ্ধ। এ জন্যে তারা নিষ্ঠুর নির্যাতনের পথ বেছে নিয়েছিল। তারা বই পুড়িয়েছে, মানুষকেও পুড়িয়ে মেরেছে। সুতরাং এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ খুব স্বাভাবিক এবং ইউরোপে তাই হয়েছে। তারা গীর্জার জোয়াল থেকে এমনভাবেই নিজেদের মুক্ত করেছে যে, এখন গড্ডালিকা প্রবাহে ভেসে চলেছে আরেক ধ্বংসের দাকে। যা হোক, মুসলমানদেরকে কেন এই কালো ইতিহাসের পরিণাম ভোগ করতে হবে? ইসলাম কেন নির্বসিত হবে স্রেফ মসজিদে কিংবা মানুষের বিবকের সীমিত পরিসরে? কিন্তু মসজিদও আজ নিরাপদ নয়। সেখানেও জিহ্বাকে আংটাবদ্ধ রাখতে হয়। কেননা গুপ্ত পুলিশের কড়া নযর থাকে এগুলোর ওপর। মোটকথা মসজিদেও আজকাল ইসলামের বিপ্লবী ব্যাখ্যা দেয়ার অনুমতি নেই।
এই সমস্যার মৌলিক কারণ, মুসলমানদের ওপর চাপিয়ে দেয়া সেক্যুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষতা। ধর্মনিরপেক্ষতা ধর্মকে রাষ্ট্র, আইন প্রণয়ন ও ক্ষমতা থেকে বিচ্ছিন্ন রাখার শিক্ষা দেয়। মুসলিম উম্মাহর সামগ্রিক ইতিহাসে এরূপ অদ্ভুত শিক্ষার কোন নযীর নেই। কোননা আশ-শারীয়াহ শুধু ইবাদত-বন্দেগীর ভিত্তি নয়, বরং আইন, লেনদেন, ঐতিহ্য ও রীতি-নীতিরও উৎস। একথা সত্যি, কোনো কোনো মুসলমান শাসক সত্য পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছেন; কিন্তু অন্তত বিচার-আচারের ক্ষেত্রে শরীয়তকে উপেক্ষা করার তেমন নযীর নেই। এমনকি হাজ্জাজ বিন ইউসুফের মতো স্বেচ্ছাচারী শাসকও কুরআনুল কারীম ও সুন্নাহর ভিত্তিতে প্রদত্ত রায়কে অগ্রাহ্য করার ধৃষ্টতা দেখাতেন না। এই পার্থক্যটা অনুধাবনযোগ্য। ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি বা অবহেলার কারণে শরীয়ত থেকে বিচ্যুত হওয়া এক কথা আর আল্লাহর বিধান হিসেবে অন্যান্য মতবাদের সত্যতা ও শ্রেষ্ঠতা অস্বীকার করা ভিন্ন কথা। এদিকেই ইঙ্গিত দিয়ে আল্লাহ্ বলছেন: “নিশ্চিত বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য বিধান দানে আল্লাহ্ অপেক্ষা কে শ্রেষ্ঠতর?” (৫:৫০)
আরেকটি ব্যতিক্রমী বিষয় মুসলিম তরুণদের পীড়া দেয়। অমুসলিম দেশগুলো তাদেরই আদর্শ ও দর্শন মোতাবেক জীবন ধারা গড়ে তুলছে, অথচ কেবল মুসলমানরাই তাদের বিশ্বাস ও বাস্তবতা, তাদের দ্বীন ও সমাজের মধ্যে সৎঘাত জারি রেখেছে। আমার একটি বইয়ে লিখেছি: “ধর্মনিরপেক্ষতা খৃষ্টানরা গ্রহণ করতে পারে, কিন্তু তা মুসলমান সমাজে একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয়।” খৃষ্টধর্ম জীবনের জন্যে পূর্ণাঙ্গ ঐশি বিধান পেশ করতে পারে না যার প্রতি তার অনুসারীরা অঙ্গীকারবদ্ধ থাকতে পারে। খোদ বাইবেলে জীবনকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে: একটি ঈশ্বর অথাৎ ধর্ম অন্যটি সীজার অথাৎ রাষ্ট্র। এতে বলা হয়েছে: “সীজারের জন্যে নির্ধারিত বিষয় সীজারকেই চালাতে দাও আর ঈশ্বরের প্রাপ্য ঈশ্বরকে দাও।” (ম্যাথিউ-২২:২১)
সুতরাং একজন খ্রীষ্টান বিবেকের কোনরূপ দংশন ছাড়াই ধর্মনিরপেক্ষতা গ্রহণ করতে পারে। তাছাড়া তাদের পক্ষে ধর্মীয় শাসনের পরিবর্তে ধর্মনিরপেক্ষ শাসন গ্রহণ করার যুক্তি আছে। তাদের ধর্মীয় শাসনের অভিজ্ঞতা বড় নির্মম। অতীতে যাজকদের স্বেছ্ছাচারী শাসনের স্মৃতি তাদের মন থেকে মুছে ফেলা কঠিন। মুসলিম সমাজে ধর্মনিরপেক্ষতা মেনে নেয়া মানে আবাদত, বান্দেগী, আইন-কানুন, আচার-অনুষ্ঠান সবকিছুকে সর্বোতভাবে পরিত্যাগ করার শামিল। তাছাড়া বর্তমান যুগের চাহিদা পূরণে শারীয়াহ সক্ষম নয়- এই মিথ্যা দাবীর কাছে নতি স্বীকার করা। বস্তুত মানুষের রচিত আইন মেনে নেয়া মানে ঐশী বিধানের পরিবর্তে মানুষের সীমিত জ্ঞানকে শ্রেয় মনে করা, অথচ আল-কুরআন বলছে: “বল! তোমরা কি বেশি জান, না আল্লাহ্?” (২:১৪০)
এ কারণে মুসরমানদের কাছে ধর্মনিরপেক্ষতার দাওয়াত নাস্তিকতা ও ইসলাম পরিহারের দাওয়াতের সমতুল্য। শারীয়াহর পরিবর্তে একে শাসনের ভিত্তি বলে গ্রহণ করলে তা হবে সরাসরি রিদ্দাহ। এই বিচ্যুতি সম্পর্কে জনগণ নীরব থাকরে তা বড় ধরনের সীমালংঘন ও পরিষ্কার অব্াধ্যতার নযীর বলে গণ্য হবে। এর ফলে মুসলিম সমাজে অপরাধবোধ, দীনতা, হিংসা, ঘৃণা ও ক্ষোভ সৃষ্টি হতে বাধ্য। বস্তুত ধর্মনিরপেক্ষতা মূলত ঈশ্বর সম্পর্কে তাদের নিজেস্ব ধ্যান-ধারণাই ফসল। এই মতবাদের দৃষ্টিতে ঈশ্বর জগত সৃষ্টি করেছেন বটে, কিন্তু এর দেখাশোনার দায়িত্ব ত্যাগ করেছেন অথাৎ জগতের সাথে ঈশ্বরের সম্পর্কে ঘড়ির সাথে ঘড়ি-নির্মাতার সম্পর্কের মতো। ঘড়ি-নির্মাতা ঘড়ি তৈরি করে দেয়ার পর নির্মাতার সাহায্য ছাড়াই চলতে পারে, তেমনি আল্লাহ পৃথিবী নির্মাণের পর তা আপন গতিতেই চলছে। এই ধারণা এসেছে গ্রীক দর্শন থেকে। এরিস্টলের মতে আল্লাহ পৃথিবী নিয়ন্ত্রন করেন না এবং এ সম্পর্কে কিছুই খবর রাখেন না। উইল ডুরান্ট এক ধাপ এগিয়ে তাকে বলেছেন অসহায় ঈশ্বর। সুতরাং এতে আর আশ্চর্যের কী আছে, যে ঈশ্বর তার সৃষ্ট জীবের খবরই রাখেন না তিনি কী করে তাদের জীবন যাত্রার বিধান তৈরি করবেন? এ দায়িত্ব ছেড়ে দেয়া ছাড়া তো তার গত্যন্তর নেই! ইসলামের ধারনা থেকে এই ধারণা সম্পূর্ণ বিপরীত। আমরা মুসলমানরা বিশ্বাস করি আল্লাহ্ একই সাথে জগতের সৃষ্টিকর্তা, বিধানদাতা ও পালনকর্তা : “... তিনি সবকিছুর বিস্তারিত হিসাব রাখেন।” (৭২:২৮)
তিনি সর্বশক্তিমান ও সর্বদর্শী; তাঁর দয়া ও বদান্যতা সকলের জন্য যথেষ।ট। এই ক্ষমতা বলেই তিনি মানুষের ঐশী পথ রচনা করছেন, হালাল-হারাম নির্ধারণ করে দিয়েছেন এবং বান্দাদেরকে তাঁরই বিধান মেনে চলতে এবং সেই অনুযায়ী ফায়সালা করার নির্দেশ দিয়েছেন। যদি তারা না করে তবে তা হবে কুফরী ও সীমালংঘন।
নিষ্ঠাবান মুসলিম তরুণরা এ ধরনের অনাচার তাদের চোখের সামনেই দেখেছে কিন্তু কিংকর্তব্যবিমূঢ়। তারা শক্তি প্রয়োগ কিংবা গলাবাজি করে এ সবের পরিবর্তন করতে পারছে না। তাদের একমাত্র উপায় মনের মণিকোঠায় গভীর অনুভূতি পোষণ যা ঈমানের দুর্বলতম অঙ্গ। অবশ্য, এই হৃদয়াবেগ চিরদিন চাপা থাকবে না। একদিন না একদিন তার বিস্ফোরণ ঘটবেই।
এছাড়া ইসলামী বিশ্ব ও মুসলমানদের পবিত্র স্থানসমূহ সর্বগ্রাসী হামলার শিকার। ইহুদীবাদ, খৃষ্টবাদ, পৌত্তলিক, মার্ক্সবাদী তথা সকল ইসলাম বিরোধী শক্তি তাদের মত পার্থক্য ভুলে একযোগে প্রকাশ্যে অথবা গোপনে ইসলামী পুনরুজ্জীবন, ইসলামী আন্দোলন অথবা ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে হীন তৎপরতা চালিয়ে যাছ্ছে। এ কারণে সকল অনৈসলামী ইস্যু প্রাচ্য ও প্রতীচ্য, বিশেষত আমেরিকা ও রাশিয়ার নৈতিক ও বৈষয়িক মদদ পায়, কিন্তু ইসলামী ইস্যুতে তারা নির্বিকার। আল্লাহ তায়ালা কুরআন মজীদ বলছেন: “বেঈমনারা একে অন্যের সমর্থক।” (৮:৭৩)
কিন্তু ভাষা-বর্ণ-গোত্র-স্থান-কাল-নির্বিশেষে মুসলমানরা অন্য মুসলমানের বিপদাপদে, নিগ্রহ নিষ্পোষণ ও হত্যাযজ্ঞে নীরব থাকতে পারে না। কারণ তারা সেই সবূত্তোম উম্মাহর অন্তর্ভুক্ত যারা একই ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ। কেননা যে মুসলমানের মনে অন্য মুসলমানের সম্পর্কে কোনো অনুভূতি নেই, সে মুসলমান নয়।
প্রতিদিন খবর আসছে ফিলিস্তিন, লেবানন, আফগানিস্থান, ফিলিপাইন, ইরিত্রিয়া, সোমালিয়া, সাইপ্রাস ও ভারতে মুসলমানরা কিভাবে নিগৃহীত হচ্ছে। অথচ আমরা দেখি আজকাল অন্য কোনো মুসলিম দেশ এ ব্যাপারে কোনো উচ্চবাচ্য করে না, বরং সম্পূর্ণ উদাসীন। আরো মর্মান্তিক, কোনো কোনো শাসক ইসলামের শত্রুদের সাথে গাঁটছড়া বাঁধেন। তারা স্রেফ গোত্রীয়, আঞ্চলিক বা জাতিগত স্বার্থ রক্ষায় ব্যস্ত।
আল্লাহ, তাঁর রাসূল, দ্বীন, উম্মাহ ও এর স্বার্থের প্রতি তাদের কোনো আনুগত্য বা অনুভূতি নেই। তরুণরা আরো লক্ষ্য করছে, ইসলামের প্রতি শাসকদের এই নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির নেপথ্যে কাজ করছে ইহুদী, খ্রীষ্টান ও কম্যুনিজমের চক্রান্ত। কিন্তু শাসকদের মনে ভীতি সৃষ্টিকরে এবং তাদেরকে ইসলামী আন্দোলনদমনে প্ররোচিত করে।
বহুবিধ বিষয়ের মধ্যে আরেকটি বিষয় বিগত কয়েক বছরে মুসলিম তরুণদের মদ্যে হতাশা সৃষ্টি করেছে। এটি হচ্ছে ১৯৬৭ সালের ৬ দিনব্যাপী মিসর-ইসরাঈল যুদ্ধ। এই যুদ্ধের মারাত্মক প্রতিক্রিয়া রোধের লক্ষ্যে যুদ্ধের জন্য দায়ি ব্যক্তিরা এই আশ্বাস বাণী শোনালেন যে, এটা “পূর্বাবস্থায় প্রত্যাবর্তন”- তেমন ক্ষতিকর কিছু নয়। অথচ আরব দেশগুলোর তরুণরা শৈশব থেকে এই অঞ্চলে চালিয়ে দেয়া হয়েছে এবং এই এলাকাকে মুক্ত করা মুসলমানদের ধর্মীয় ও জাতীয় দায়িত্ব। ফিলিস্তিনের গ্রান্ড মুফতী মরহুম আমীন আল-হুসয়নী (র) -এ ব্যাপারে বলেছিলেন, “ফিলিস্তিন জনবসতিহীন জনপদ নয় যে, এখানে জনপদহীন লোকদের আশ্রয় দিতে হবে।” যা হোক ১৯৬৭ সালের যুদ্ধে শোচনীয় পরাজয়ের পর পরিস্থিত নতুন মোড় নিলো অথাৎ আগ্রাসনের ক্ষতি কাটিয়ে ওঠার নামে ইসরাঈলকে স্বীকৃতি দেয়ার মতো পরিস্থিতি সৃষ্টির কৌশল অবলম্বন কর হলো। এর অর্থ দাঁড়ায়, সাম্প্রতিক ইসরাঈলী আগ্রাসনে পুরানো আগ্রাসনকে বৈধ বলে স্বীকার করে নেয়া হয়। যদি তাই হয়, তাহলে ১৯৪৯, ১৯৫৬ ও ১৯৬৭ সালের যুদ্ধের কী কারণ ছিল? গোড়াতেই ইসরাঈলকে স্বীকৃতি দিলে মুসলিম উম্মাহ মারাত্মক পরিণতির হাত থেকে রেহাই পেতো। বস্তুত তথাকথিত “শান্তিপূর্ণ সমাধান” ও শান্তিচুক্তির অজুহাতে এসব অবমাননাকর উদ্যোগ নেয়া হয়। ক্ষমতাসীন কর্তৃপক্ষ সামরিক, রাজনৈতিক, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিকে সামনে রেখে তাদের নীতির পক্ষে সাফাই দেন। কিন্তু এসবই মুসলমানদের আশা-আকাংখায় তীব্র আঘাত হানে, বিশেষ কর ইসরাঈলের প্রতি সকর বৃহৎ শক্তির স্বীকৃতি ও সমর্থন এবং মুসলিম স্বার্থের প্রতি উপেক্ষা মুসলমানেদের আঘাত তীব্রতর করে। এসব ঘটনা থেকে এই উপসংহার টানা যায় যে, ইসলামের বিরুদ্ধে নতুন করে ক্রুসেড শুরু করা হচ্ছে। এসরামী বিশ্ব ও ইসরামী আন্দোলনের প্রতি পাশ্চাত্য ও পাশ্চাত্যের রাজনৈতিক নেতাদের মনোভাবে এটা পরিস্ফুটিত। মুসলমানদের সাথে শতাব্দী প্রাচীন লজ্জাকর লড়াইয়ের স্মৃতি তাদের মনে এখন তরতাজা রয়েছে। তাই তাদের অন্তরে এখনো মুসরিম বুদ্ধিজীবি অবশ্য এই ধারণা বাতিল করে যুক্তি দেখাতে চান যে, পাশ্চাত্যে ক্রুসেড চেতনা নয়, তাদের জাতীয় স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখেই সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু সাম্প্রতিক পরিস্তিতি তাদের এই দাবীকে ভুল প্রমাণিত করেছে, বরং পাশ্চাত্যে ক্রুসেড চেতনা পূর্ণমাত্রায় জীবন্ত। আমি আমি এলেনবী অথবা জেনারেল গুরান্ডের কথা বলতে চাই না। আমাদের সমসাময়িকদের মনেই প্রশ্ন জেগেছে : কেন পাশ্চাত্য মুসলিম ভূখন্ডে ইসরাঈলের অস্তিত্ব বহাল রাখতে আগ্রহী? কেন যুক্তরাষ্ট্র ইসরাঈলের নিন্দা সম্বলিত প্রতিটি জাতিসংঘ প্রস্তাবে ভেটো দেয়? কেন তারা ইরিত্রিয়ার বিরুদ্ধে মার্ক্সবাদী ইথিওপিয়াকে সমর্থন যোগায়? কেন সংবাদপত্রে মুসলিম দেশের ঘটনাবলী গুরুত্ব সহকারে স্থান পায় না? অথচ বিশ্বের কোথাও একটি বিমান হাইজ্যাক হলে যেন তুলকালাম কান্ড শুরু হয়? কেন তারা অন্যদের চেয়ে আরবদের সস্তা মনে করে? আসলে এগুলোর কোনো ব্যাখ্যা নেই। প্রকৃতপক্ষে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ইহুদীবাদ, খৃষ্টবাদ ও কম্যুনিজমের শয়তানী আঁতাত গড়ে উঠেছে।
বস্তুত মুসলিম তরুণদের মতে মুসলিম দেশগুলোর শাসকরা বিদেশী শক্তির দাবার গুটিমাত্র। তাদেরকে সামরিক অভ্যুথ্থানের মাধ্যমে ক্ষমতায় এনে মুসলমানদের চৌখে ‘হীরো’ সাজানো হয়। এই ধারণার মধ্যে অতিশয়োক্তি থাকলে থাকতে পারে, কিন্তু সামগ্রিক ঘটনা প্রবাহের আলোকে একেবারেই ভিত্তিহীন নয়। এসব ঘটনা চোখে আয়্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় যে, ইসলামী পুনর্জাগরণ অঙ্কুরে বিনষ্ট করার জন্যেই এই শাসকরা শয়তানী চক্রের ফাঁদে পা দিয়েছে। এই নেতারা দৃশ্যত মুসলমান ও ইসলামের জন্যে কুম্ভীরাশ্রু বর্ষণ করে, আসলে তারা মুসলিম উম্মাহর শত্রুদের পোষা এজেন্ট।
৯. ইসলামী দাওয়াতে প্রতিবন্ধকতা
আরেকটি বিষয়ের দিকে আমাদের দৃষ্টি দেয়া দরকার। বিষয়টি হচ্ছে ইসলাম প্রচারে স্বাধীনতা। ইসলাম শুধু নিজেকে সৎ হিসেবে গড়ে তোলার শিক্ষা দেয় না, অন্যকেও সংশোধনের তাগিদ দেয়। মানুষকে ভাল কাজের আদেশ দেয় ও খারাপ কাজ থেকে বিরত প্রচেষ্টাকে এ কারণে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। তাই প্রত্যেক মুসলমানকে তার সামর্থ অনুযায়ী ইসলাম প্রচারের কাজে অংশ নিতে হবে। এ জন্যে কুরআনে বলা হয়েছে: “তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের পথে আহবান করো।”...(১৬: ১২৫)
রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রত্যেক সাহাবী ছিলেন ইসলাম প্রচারক (দাইয়া)। কুরআন আরো বলছে: “বল, এটাই আমার পথ: আল্লfহর প্রতি মানুষকে আমি আহবান করি সজ্ঞানে। আমি ও আমার অনুসারীগণ।” (১২:১০৮)
অতএবসংস্কার কর্মীদের লক্ষ্য হচ্ছে: “নিজে সৎ হও অপরকে সৎ করো।” আলকুরআনের ভাষায়: “কে উত্তম আল্লাহ্র (সাহায্যের) হাত জামা’তের সাথেই থাকে।” তিনি আরো বলেন: “একজন ঈমানদার আরেকজন ঈমানদারের কাছে সেই ইমারতের মতো যার বিভিন্ন অংশ একে অপরের সাথে সংযুক্ত।” (বুখারী)
নিজেদের মধ্যে সহৃদয় সহযোগিতা এবং সৎ কাজের আদেশ কেবল একটি ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা নয়, বরং একটি অপরিহার্য শর্ত। অতএব দাওয়াতী ক।ষেত্রে সামষ্টিক কাজ বাধ্যতামূলক- এছাড়া দায়িত্ব অপূর্ণ থাকে। বাস্তব কথা হচ্ছে ইসলাম বিরোধী শক্তি বিভিন্নভাবে সংগঠনের মাধ্যমে কাজ করছে, অতএব মুসলমানদেরকেও সংঘবদ্ধ হয়েই ঐ শক্তির মোকাবিলা করতে হবে। আন্যথায় আমরা পিছিয়ে পড়তে থাকব যখন অন্যরা এগুতে থাকবে। অতএব যেসব মুসলিম দেশে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে পরিচালিত দাওয়াতী কাজের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হয়, সরকারীভাবে এমনকি সেন্সরশীপের মাধ্যমে তারা মস্ত বড় গুনাহ করে। দাওয়াতী কাজে ভীতি প্রদান ও বাধা সৃষ্টিও চরমপন্থী মনোভাব সৃষ্টির প্রধান কারণ, বিশেষ করে যখন ধর্মনিরপেক্ষতা ও মার্ক্সবাদ প্রচারে কোনো বাধা দেয়া হয় না; বরং সকর সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়া হয় তখন এটাকে কিছুতেই সহজভাবে মেনে নেয়া যায় না। এটা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক এ কারণে যে, মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে ইসলামী বিপ্লবের কাজে বাধা দেয়ার অধিকার কারো নেই, কোনো সরকারেরও থাকতে পারে না।
বস্তুত মুসলিম দেশগুলোতেই ইসলামকে পরিপূর্ণ জীবন বিধান হিসেবে প্রতিষ্ঠার চেষ্ঠা করতে গিয়ে সেন্সরশীপ ও নানা রকম দলনের শিকার হতে হচ্ছে। সেখানে ইসলামের চেহারা হচ্ছে পশ্চাদপদতা ও অবজ্ঞায় এবং আচার-অনুষ্ঠান, বিদাতী কাজ কাম, শাসক-তোষণ এবং শাসকদের গদী বহাল রাখার দেয়ার মধ্যে সীমিত। আর দুর্নীতিপয়ারণ শাসকরাও এ ধরনের ইসলামের পৃষ্ঠপোষকতায় অতি উৎসাহী। এভাবে অন্যায়-অবিচার শোষণ-নির্যাতনের বিরুদ্ধে জিহাদকে তারা স্যাবোটাজ করার অপচেষ্টা চালায়। মার্কস সম্ভবত এই অর্থে দাবী করেছিলেন, “ধর্ম জনগণের জন্যে আফিম।”
কিন্তু কুরআনুল করীম, সাহাবায়ে কিরাম, তাবিঈন যে ইসলাম রেখে গেছেন তা হচ্ছে সত্য, শক্তি, সম্মানান-মর্যাদা, ত্যাগ-তিতিক্ষা ও জিহাদের প্রতিভূ। আর শাসকরা এই ইসলামকে ভয় পায়; কারণ তাদের অনাচার-অবিচারের বিরুদ্ধে কি জানি কখন বিদ্রোহ দেখা দেয়! পক্ষান্তরে এই ইসলাম তার অনুসারীদেরকে বলে: “তারা আল্লাহর বাণী প্রচার করতো এবং তাঁকে ভয় করতো, আর আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করতো না।” (৩৩:৩৯)
এই পরিছন্ন বিশ্বাসের আলোকে ঈমানদাররা মনে করে যেহেতু জীবন মেয়াদ আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত, অতএব কাউকে ভয় করার দরকার নেই, আর তিনি ছাড়া কারো কাছে পার্থনারও দরকার নেই। সমসাময়িক তুরস্কের একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। একবার একজন উপপ্রধান মন্ত্রীকে মন্ত্রণালয় থেকে কারাগারে নিয়ে যাওয়া হয়। তিনি একটি দলের নেতা। তাদের বিরুদ্ধে শরীয়ত প্রবর্তন করার দাবী জানানোর অভিযোগ আনা হয়। অথচ তুরস্কের ৯০ ভাগ মানুষ মুসলমান! উক্ত নেতা ও তার অনুসারীদের বিরুদ্ধে ১৫টি অভিযোগ খাড়া করা হয়। অভিযোগগুলোর মূল বিষয় ছিলো তারা ধর্মনিরপেক্ষ তুরস্ককে এসলামী রাষ্ট্রে পরিণত করতে চান। ধর্মনিরপেক্ষ আতাতুর্কের অনুসারী তুরস্কের তদানীন্তন সামরিক সরকার শরীয়ত তথা আসলামী জীবন বিধান পুনঃপ্রবর্তনের যে কোন প্রচেষ্টাকে অপরাধ বলে গণ্য করে। অথচ উক্ত গ্রুপ সর্বসম্মত আইনানুগ পন্থায় গণতান্ত্রিক পরিবেশে তাদের কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। তারা শক্তি প্রয়োগ করে সহিংস পন্থায় সরকার উৎখাত করতে চাননি। সামরিক কৌশুলী তাদের বিরুদ্ধে নানা আপত্তিকর শ্লোগান তোলার অভিযোগও উথ্থাপন করে। শ্লোগানগুলো ‘আশাশারীয়াহ এবং ইসলাম এক ও অভিন্ন’ এবং আল-কুরআনই হচ্ছে সংবিধান।’
প্রশ্ন হচ্ছে, কোনো মুসলমানই যিনি আল্লাহকে প্রভু, ইসলামকে দ্বীন ও হযরত মুহাম্মদ (সা) কে রাসূল হিসেবে স্বীকার করেন তার পক্ষে কী এগুলো অস্বীকার করা সম্ভব? যখন ঈমানের পরিবর্তে কুফর এবং হারামকে হালাল করা হয় তখন মুসলমানদের কীকরা উচিত? এসব অস্বাভাবিক পরিস্থিতি কী বাড়াবাড়ি ও চরমপন্থার মূল কারণ নয়? একটি আফ্রো-আবর দেশে কম্যুনিস্ট তৎপরতার জন্যে সাংবিধানিক সুযোগ ও নিরাপত্তা দেয়া হয়েছে। কিন্তু ইসলামী ভাবধারা জাগ্রত করার সকল প্রচেষ্টা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অথচ ঐ দেশটি নিজেকে তথাকথিত “স্বাধীন বিশ্বের অঙশ” বলে বিবেচনা করে। আরো মারাত্মক হচ্ছে ঐ দেশটির মুসলিম নেতা-কর্মীদেরকে কারাগারে নিক্ষেপ করে নিষ্ঠুর নির্যাতন চালানো হচ্ছে। তাদের বিরুদ্ধেও একমাত্র অভিযোগ, তারা আল্লাহ্ কে প্রভু, সত্যকে লক্ষ্য, ইসলামকে একমাত্র পথ, কথাকে অস্ত্র এবং জ্ঞানকে তাদের একমাত্র খোরাক বলে ঘোষণা করেছিলো।
অতএব, হেকমত ও সুন্দর ভাষণের মাধ্যমে ইসলাম প্রচারে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে তরুণরা যদি শক্তিকে ও সহিংসতাকে সহিংসতা দিয়ে মোকাবিলা করতে চায় তাহলে কি তাদের দোষ দেয়া যায়? এই অবস্থা চলতে দেয়া যায় না। ইন্ শাআল্লাহ ইসলাম যেভাবে হোক সংঘবদ্ধভাবে এগিয়ে যাবে। তাদেরকে সুস্থ ও স্বাধীন পরিবেশে কাজ করতে দেয়া উচিত। অন্যথায় ঘটনাবলী অবাঞ্ছিত বিপরীত খাতে প্রবাহিত হতে পারে। খোলাখুলি কাজ করতে না দিলে দাওয়াতী কাজ বিভ্রান্তিকর গোপন সহিংসতা কিংবা চরমপন্থার রূপ নিতে পারে। ক্ষমতাসীন কর্তৃপক্ষের মারাত্মক ভুল হচ্ছে তারা ইসলামী আন্দোলন দমনে বন্দী শিবির সহিংস মানসিক ও শারীরিক নির্যাতনের আশ্রয় নেয়। বন্দীশিবিরগুলোতে মানুষের সাথে পশুর মতো আচরণ করা হয়। এ প্রনঙ্গে ১৯৫৪ ও ১৯৬৫ সালের মিসরের ঘটনা স্মরণ করা যেতে পারে। সামরিক কারাগারে ইসলামী বিপ্লবের নেতা ও কর্মীদেরকে লোমহর্ষক ও অবিশ্বাস্য পন্থায় শাস্তি দেয়া হয়। এখনো এসব কথা দুঃস্বপ্নের মতো মনে হয়। তাদের দেহে আগুন ও সিগারেটের ছ্যাঁক দেয়া হয়, নারী ও পুরুষ বন্দীকে জবাই করা পশুর মতো ঝুলিয়ে রাখা হয়, কারারক্ষীরা পালাক্রমে রক্ত ও পুঁজ জমে না ওঠা পর্যন্ত বন্দীদেরকে আগুনে ঝলসাতে থাকে। এই পাশাবিক আচরণে অনেকেই শাহাদত বরণ করেন। কিন্তু শাস্তিদাতাদের দিল আল্লাহর ভয়ে এতোটুকু কেঁপে ওঠেনি। নাৎসীবাদ, ফ্যাসিবাদ ও সমাজবাদের উদ।ভাবিত সকর নির্যাতন কৌশল তারা নির্বাচারে আল্লাহ্র পথের মুজিহিদদের ওপর প্রয়োগ করে।
এই বন্দীশালায় চরমপন্থা ও তাকফীরের প্রবণতা জন্ম নেয়। বন্দীদের মনে প্রশ্ন জাগে : আমরা কি অপরাধে হচ্ছি? আমরা আল্লাহর কালামের কথা ছাড়া আর কিছুতো বলিনি? আল্লাহর পথে জিহাদে আমরা কেবল আল্লাহ্ রই সাহায্য চেয়েছি, অন্য কারো কাছে তো পুরস্কার বা প্রসঙসা চাইনি? এই প্রশ্ন আরো প্রশ্নের জন্ম দেয়। এই পশুরা কে যারা আমাদের নির্যাতন করে, আমাদের মানব সত্তাকে অপমানিত করে, আমাদের ধর্মকে অভিশাপ দেয়, আমাদের প্রভুরও অমর্যদা করার মতো ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে! একজন পদস্হ কর্মকর্তা একদিন বলে: ‘তোমাদের প্রভুকে আমার কাছে হাযির করো, তাকে আমি জেলে পুরব।” এই পশুগুলোকে কি মুসলমান বলা চলে? এরা যদি মুসলমান হয় তাহলে কুফরী কী? এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, এরাই হচ্ছে কাফির, এদেরকে ইসলামের আওতা থেকে বিতাড়িত করতেই হবে। এরপর আরো প্রশ্নের উদয় হয়: এদের সম্পর্কে এই যদি হয় আমাদের বিচার, তাহলে এদের মনিব সম্পর্কে আমরা কি সিদ্ধান্ত নেবো? ক্ষমতার আসনে বসে যেসব নেতা ও শাসক ইসলামী বিপ্লবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে তাদেরকেই বা কিভাবে বিচার করা উচিত? তুলনামূলক বিচারে তাদের অপরাধ অধিকতর মারাত্মক এবং তাদের রিদ্দাহ আরো স্পষ্ট- যে সম্পর্কে কুরআনুল করীমে বলা হয়েছে: “আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুসারে যারা বিধান দেয় না তারা সত্যত্যাগী।” (৫:৪৭)
এই সিদ্ধান্তে আসার পর ঐ নির্যাতিত মুসলমানরা তাদের সহবন্দীদের কাছে প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয়: যেসব শাসক আল্লাহ্র বিধান মোতাবেক বিচার করে না এবং যারা শরীয়তের বাস্তয়নে সংগ্রামরত তাদের সাথে একমত হলো তাদেরকে শত্রু গণ্য করলো। এমনকি কাফিরও মনে করলো, কেনা কাফিরের কুফরী সম্পর্কে যে সন্দেহ পোষণ করে সে নিজেই কাফির। কিন্তু একানে শেষ নয়। যেসব লোক ঐরূপ শাসকের আনুগত্য করে তাদের সম্পর্কেও প্রশ্ন উঠলো। জবাব তৈরি ছিলো: তাদের শাসকের আনুগত্য করে সে নিজেও কাফির।
এভাবে ব্যক্তি গ্রুপ বিশেষকে কুফরী ফতোয়া দেয়ার্ প্রবণতা মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো। লক্ষণীয় ব্যাপার হচ্ছে, সহিংসতা শুধু সহিংসতার জন্ম দেয় না, সুস্থ চিন্তাকেও দূষিত করে এবং ঐ দলন-দমন অর্নিবার্য বিদ্রোহের জন্ম দেয়।
পরিভাষা সঙ্কেত
১. সুনান: রীতি, ধারা।
২. তালিব আল-হাদীস:
যে বৈশিষ্ট্য ও পরিস্থিতিতে হাদীস অশুদ্ধ হতে পারে সেই সংক্রান্ত শাস্ত্র।
তৃতীয় অধ্যায়
চরমপন্থার প্রতিকার
এখন আমরা চরমপন্থার প্রতিকার এবং তার উপায় ও পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করবো। প্রথমেই এ বিষয়টি বুঝে নেয়া দরকার যে, প্রতিকার চরমপন্থার কারণ থেকে অবিচ্ছিন্ন। এর কারণগোলো যেমন বিভিন্ন ও জটিল তেমনি এর প্রতিকারগুলোও। বলা বাহুল্য, কোনো যাদুস্পর্শে চরমপন্থার অবসান ঘটানো যাবে না কিংবা তাদেরকে মধ্যপন্থা ফিরিয়ে আনা যাবে না। আমাদের কাছে চরমপন্থা ও গোঁড়ামি-এর মনস্তাত্ত্বিক, সামজিক ও রাজনৈতিক দিকসহ একটি অদ্ভুত ধর্মীয় সমস্যা। সুতরাং ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে এর সবগুলো দিক বিবেচনা করতে হবে।
আমি তাদের সাথে একমত নই যারা কেবল সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থাকে এই অদ্ভুত সমস্যার কারণ বলে চিহ্নিত করে যুব সমাজের আচরণ ও পদক্ষেপগুলো উপেক্ষা করতে চান। আবার সমাজ, সরকার, সরকারী বিভাগ, বিশেষত শিক্ষা ও প্রচার মাধ্যমকে সকল দায়-দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়ে কেবর যুব সমাজকে দোষ দেয়া অন্যায়। দায়িত্বটা আসলে পারস্পরিক এবং প্রতিটি পক্ষের একেকটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, “তোমরা সকলে তোমাদের সন্তান-সন্ততি ও অধীনস্থ ব্যক্তিদের অভিভাবক এবং দায়িত্বশীল।” (বুখারী)
আমরা এখন চরমপন্থা কাটিয়ে ওঠার ব্যাপারে সমাজের পরিপূরক ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করবো। আমি আগেই বলেছি, বর্তমান যুগের অন্তর্গত পরস্পর বিরোধিতা ও অরাজক অবস্থা এবং ইসলাম থেকে মুসলমানদের বিচ্যুতি চরমপন্থা প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। অতএব, এই সামজকেই এর প্রতিকারে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে হবে। প্রাথমিক পদক্ষেপ হচ্ছে, ইসলামের প্রতি তাদের আন্তরিক, সুদৃঢ় ও সুষ্পষ্ট অঙ্গীকার নবায়ন করা। এটা কেবল মৌখিক ঘোষণা, কিছু মনোহর শ্লোগান অথবা সংবিধানে ‘ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম’ ঘোষণা করে নয়, বরং ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার ঘনিষ্ঠ অনুসরণের মাধ্যমেই সম্ভব।
আমরা জানি, ইসলাম এমন একটি সার্বিক জীবন বিধান যা মানুষের মধ্যে ঐশী বৈশিষ্ট্যকে বিকশিত করতে চায়। এ জন্যে ইসলাম জীবনকে সঠিক পথে পরিচালনা ও বিচ্যুতি থেকে রক্ষার লক্ষ্যে আদর্শিক কাঠামো, পথ-নির্দেশ ও সীমারেখা নির্ধারণ করে দিয়েছি। এর আওতায় থাকলে মানুষের এবাদত-বন্দেগী, মনমানস, আইন-বিধান এক সৌন্দর্যময় রূপ লাভ করে, এক সুবিচারপূর্ণ সমাজ গড়ে ওঠে। তাই প্রকৃত ইসলামী আদর্শের বাস্তবায়ন করতে হবে। ইসরাঈলদের মতো খন্ডিতভাবে নয়। আল্লাহ তায়লা কুরআনুল করীমে বলেন:
“তাহলে তোমরা কি কিতাবের কিছু অংশ বিশ্বাস করো এবং কিছু অংশ প্রত্যাখ্যান করো? সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা এরূপ করে তাদের একমাত্র প্রতিফল পার্থিব জীবনে জিল্লতি আর কিয়ামতের দিনে তারা কঠিনতম শাস্তির দিকে নিক্ষিপ্ত হবে।” (২:৮৫)
সুতরাং ইসলামী চরিত্রের সমাজ কায়েম করতে হলে জীবনের সর্বক্ষেত্রে তথা সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষেত্রে আল্লাহ্ র বিধান ও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সুন্নাহ প্রয়োগ করতে হবে। এটাই ঈমানের প্রকৃত দাবী। কুরআনের ঘোষণা:
“কিন্তু না, তোমার প্রভুর শপথ! তারা মুমিন হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের নিজেদের বিবাদ-বিসম্বাদের বিচারের ভার তোমার ওপর অর্পণ না করে; অতঃপর তোমার সিদ্ধান্ত সম্পর্কে তাদের মনে কোন দ্বিধা না থাকে এবং সর্বান্তঃকরণে তা মেনে নেয়।”(২৪:৫১)
আমরা ইসলামকে ঐশী বিধান হিসেবে মানি। কিন্তু বাস্তব জীবনে শরীয়াহকে প্রয়োগ করি না। তার জায়গায় আমরা পূর্ব ও পশ্চিম থেকে ধার করা ব্যবস্থা চালু করেছি, তবুও আমরা মুসলমান বলে দাবী করি! সমাজ থেকে এই সুষ্পষ্ট পরস্পর বিরোধিতা অবশ্যই দূর করতে হবে।
সুতরাং আমেদের শাসকদের অনুধাবন করতে হবে যে, তারা মুসলিম ভূখন্ড শাসন করছেন এবং মুসলমানদের তাদের ধর্মীয় বিধান অনুসারে শাসিত হওয়ার অধিকার আছে। সামাজিক, রাজনৈতিক, বুদ্ধিবুত্তিক, সাংস্কৃতিক, আন্তর্জাতিক তথা সকল ক্ষেত্রে ইসলামী মূল্যবোধের প্রতিফলন ঘটাতে হবে।
সকল ও আন্তর্জাতিক নীতি এই বিশ্বাসের ভিত্তিতে প্রণয়ন করতে হবে। মুসলিম শাসকরা যদি এই ন্যায়সঙ্গত প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ হন তবে তা হবে চরম ইসলাম বিরোধিতার শামিল। বস্তুত এ বিষয়টির প্রতি মুসলিম শাসকদের উপেক্ষা ও ঔদাসীন্য অসহনীয় হয়ে উঠেছে। কেউ কেউ প্রকাশ্যে ইসলামী আন্দোলনকারীদের সকল সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত করেন। এই শাসকরা মসজিদকেও তাদের মতলব হাসিলের কাজে লাগান। কেউ এর বিরোধিতা করলে তাকে কঠোর শাস্তি দেয়া হয়। আবার কিছু কিছু শাসক মুসলমান বলে দাবী করেন এবং যা তাদের ধারণা নেহায়েত মনগড়া এবং শয়তানী খেয়ালখুশীর নামান্তর। যা তাদের মতলব হাসিলের অনুকূল তা গৃহণ করেন এবং তাদের পছন্দসই নয় তা নির্দ্বিধায় নাকচ করে দেন। তারা যা বিশ্বাস করেন তাকেই “সত্য” বলে ঘোষণা করেন এবং এর বিপরীত সবকিছু বাতিল। তারা কুরআন ও হাদীসের সঠিক ব্যাখ্যা অস্বীকার করে নিজেরাই এ সবের ব্যাখ্যাতা সাজেন। তারা কোনো বিজ্ঞ আলিম-ওলামার সাথে পরামর্শ করার ধার ধারেন না। তারা প্রত্যেক নিজেকে একেকজন ফকীহ, মুফাসসির, মুতাকাল্লিম ও দার্শনিক ভেবে বসেন।
এ ধরনের মুসলমান শাসক মনে করেন তাদের বিকল্প দ্বীতিয় ব্যক্তি নেই। তিনি হযরত মুহাম্মদ (সা) থেকেও কিছু শেখার প্রয়োজন অনিভব করেন না। কুরআন ব্যাখ্যার জন্যে তিনি নিজেকেই যথেষ্ট মনে করেন। অথচ আল্লাহ্ বলেন: “রাসূলের আনুগত্য করে, সে আল্লাহ্র আনুগত্য করে।” (৪:৮০)
অবশ্য এসব শাসক ব্যক্তিগত জীবনে ইসলামী শরীয়াহ প্রয়েগের অনুমতি দেন। রেডিও-টেলিভিশনে ইসলাম সম্পর্কে আলোচনার কিঞ্চিত সুযোগ দিয়ে থাকেন আর সংবাদপত্রে শুক্রবারের জন্যে একটি কালাম বরাদ্দ করেন। এখানে অলোচ্য বিষয় হচ্ছে ধর্ম কেবল ব্যক্তি সত্তা ও স্রষ্টার সম্পর্কের মধ্যে সীমিত। সমাজ ও রাষ্ট্রের সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই। এটাই হচ্ছে অধুনা মুসলিম শাসকদের বিশ্বাস অথাৎ আইন ছাড়া ঈমান, রাষ্ট্র ছাড়া দ্বীন, দাওয়াত ছাড়া ইবাদত এবং সত্যের আদেশ ও মিথ্যার নিষেধ ছাড়া জিহাদের ডাক। এখন কোনো নাগরিক যদি এদের বিরোধিতা কের ইসলামী জীবন বিধান চালুর ডাক দেয় তবে তার বিরুদ্ধে ধর্ম ও রাজনীতি সংমিশ্রণের অভিযোগ আনা হয়। মোটকথা, শাসকদের কর্যকলাপ আল্লাহ্, আল্লাহ্ র রাসূর ও তাঁর সাহাবীদের পথের বিপরীত। মুসলিম বিশ্ব এক চরম সন্ধিক্ষণে। অতএব, প্রকৃত ইসলামের প্রতি অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়ে তা প্রতিষ্ঠা করা ছাড়া সমাজে স্থিতিশীলতা আসতে পারে না. পারে না জনগণের প্রত্যাশা পূরণ করতে। উমর ইবনে খাত্তাব (রা) বলেন, “আমরা নিকৃষ্টতম জাতি ছিলাম। কিন্তু ইসলাম দিয়ে আল্লাহ আমাদেরকে স্মানিত করেছেন। যদি আমরা ইসলামকে বাদ দিয়ে অন্য পন্থায় মর্যাদা হাসিল করতে চাই তবে আল্লাহ্ আমাদের গোড়া কেটে দেবেন।” সুতরাং শারীয়াহ প্রয়োগ না করা পর্যন্ত আমাদের সমাজে চরমপন্থার বিস্তার ঘটবেই।
দ্বিতীয় পদক্ষেপ হচ্ছে, তরুণদের প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টাতে হবে। আইভরি টাওয়ার থেকে তাদের উদ্দেশ্যে মুরব্বীসুলভ ভাষণ দিলে চলবে না। তাদের মনমানসিকতা ও বাস্তবতা উপলব্ধি করে কথা বলতে হয়। নইলে তারা কথা শুনতেই অস্বীকার করবে। তাদের শুধু দোষ দিয়ে থাকেন। শুধু তাই নয়, তাদের গুণগুলো উপেক্ষা করে দোষগুলোই প্রচার করা হয়।
তৃতীয়ত, আমাদের সমাজে আরেকটি প্রবণতা রয়েছে। একটা গোষ্ঠীর কেউ একজন দোষ করলে তা সাধারণভাবে সকলের ওপর চাপানো হয়। তরুণদের বেলায় এটি আরো বেশী প্রযোজ্য। একজন তরুণ করলো কী করলো না, অমনি তা সকল তরুণদের ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়। তাছাড়া ঘটনা ভাল করে না জেনে হুট করে রায় দেয়ারও প্রবণতা আমাদের রয়েছে। ভাল করে না জেনে না শুনে সংখ্যালঘৃর দোষ সংখ্যাগুরুর ওপর চাপিয়ে দেয়া ন্যায় বিচার নয়। এজন্যে মুসলিম ফকীহরা রায় দিয়েছেন, সংখ্যাগুরুর বিরুদ্ধে যে রায় দেয়া হয় তা সার্বিকভাবে প্রযোজ্য, কিন্তু এর বিপরীতটা নয় অর্থাৎ মুষ্টিময়ের বিরুদ্ধে প্রদত্ত রায় সংখ্যাগুরুর বিরুদ্ধে প্রযোজ্য হতে পারে না। একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে একজনের সামগ্রিক কর্মকান্ডের বিচার হতে পারে না। তার সামগ্রিক আচরণের মূল্যায়ন করেই তার সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া যায়। কারণ কুরআন বলছে: “যার (সৎকর্মের) পাল্লা ভারী, সেই মুক্তি পাবে।” (২৩:১০২)
চতুর্থ, নিছক ব্যক্তিগত বিশ্বাস দিয়ে তরুণদের বিচার করা ঠিক নয়। তাদেরকে অনেক মানসিক রোগজনিত খামখেয়ালি বলে ভাবেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এটা সত্য হতে পারে; কিন্তু সামগ্রিকভাবে সন্দেহাতীত। আসলেই তাদের ঈমান ও আচরণে কোনো দ্বৈততা নেই। আমি অনেক মুসলিম দেশের অনেক তরুণের কথা জানি, তারা ঈমানী জযবায় সুদৃঢ় এবং আমলে-আচরণে সত্যনিষ্ঠ। সত্যের প্রতি তাদের নিষ্ঠা ও মিথ্যার প্রতি তাদের র্ঘণাকে আমি প্রশংসাকরি। তারা সমাজে ইসলামী মূল্যবোধ ও শারীয়াহ প্রতিষ্ঠার জন্যে কঠোর জিহাদে নিমগ্ন। এই তরুণদের সাথে মেলামেশা করে আমার স্থির বিশ্বাস জম্মেছে যে, আমাদের পোচলিত ইসলামী ধ্যান-ধারণার সাথে তাদের চিন্তাধারার মৌলিক পার্থক্য আছে। তারা এক নতুন উদ্দীপ্ত ইসলামের প্রতি অঙ্গীকারাবদ্ধ যে ইসলাম আমাদের মতো জরাজীর্ণ নয়; তাদের ঈমান সতেজ, আমাদেরটা ঠন্ডা; তাদের সাধুতা সুদৃঢ়, আমাদেরটা করুণ। তাদের হৃদয়ে আল্লাহ্ র ভয় সদাজাগ্রত- তাদের হৃদয় কুরআনের তিলাওয়াতে সদা স্পন্দিত। তাদের মধ্যে কেউ কেউ সারা রাত ইবাদতে মগ্ন থাকে, দিনে রোযা রাখে, প্রত্যুষে আল্লহ্ র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে। এসব দেখে আমার পূর্ণ বিশ্বাস জন্মেছে যে, ইনশাআল্লাহ্ ইসলাম আবার স্বীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হবে। এ জন্যেই আমি মিসরে বিভিন্ন উপলক্ষে ঘোষনা করেছি, এই তরুণ গোষ্টীই মিসরের প্রকৃত আশার আলো। যে কোনো বৈষয়িক সম্পদের চেয়ে এরা অধিক মূল্যবান।
তাই আমি বিশ্বাস করি, চরমপন্থার প্রতিকার অন্বেষণে আমাদের কথাবার্তায় আচরণে বারসাম্য, সুবিবেচনা ও উদারতা থাকতে হবে। এলোপাথাড়ি অতশয়োক্তি এই অদ্ভুত সমাধানের সহায়ক হবে না, করং এই প্রকণদা ত্রাস সৃষ্টি করে। সবচেয়ে বড় কথা, সত্য ও প্রকৃত ঘটনাকে বিকৃত, বিচারের মানদন্ডকে দোদুল্যমান এবং সুস্থ চিন্তাকে দূষিত করে। ফলত কনো, তা অন্যায় কিংবা অন্তত অসম্পূর্ণ হতে বাধ্য।
তাথাকথিত “ধর্মীয় চরমপন্থা” এবং সরকার ও তরুণদের মধ্যে সংঘাতের ফলে উদ্ভুত সংকট মুকাবিলার প্রক্ষিতে যা কিছু বলা বা লেখা হচ্ছে তা বাড়াবাড়ি ও অতিশয়োক্তি মুক্ত নয়। তরুণদের বিরুদ্ধে অনেক মানুষ অসদুদ্দেশ্য-প্রণোদিত মনোভাব পোষন করে। ঐসব বক্তব্যে এর প্রভাব লক্ষণীয়। এই প্রসঙ্গ নিয়ে একজন সমাজবিজ্ঞানী ড. সাদ আল দ্বীন ইবরাহীম ‘আল-আহরাম’ পত্রিকায় লিখেছেন: যারা এই প্রচারণায় অংশ নিয়েছেন তারা আসল সত্যের ধারে কাছেও নেই। তাদের যুক্তির কোনো সুনিদৃষ্ট ভিত্তিও নেই। তাদের বক্তব্যে অজ্ঞতা ও চরম অবিবেচনাপ্রসূত দৃষ্টিভঙ্গি প্রকট। প্রকৃতপক্ষে এই সমস্যার প্রশ্নে এদের নিশ্চুপ থাকাই শ্রয় ছিলো, নতুবা বাস্তব দৃষ্টিকোন থেকে সমস্যার বিশ্লেষণ করা উচিত ছিলো। কিন্তু এই গুণ বৈশিষ্ট্য তো এদের মধ্যে নেই। এ ব্যাপারে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে, ধর্মীয় ব্যাপারে এসব লোকের মুক্তকচ্ছ, শিথিল ও ঔদাসীন্যের চরমপন্থী মনোভাবই ধর্মীয চরমপন্থা সৃষ্টিতে সহায়ক হয়েছে। মোটকথা, এক শ্রেনির লোকের চরম বিরাগ আরেক শ্রণিকে চরম অনুরাগী করেছে। যদা কোনো বিজ্ঞ প্রচেষ্টা উভয়পক্ষের মতভেদ দূর করে তাদেরকে একত্র করতে ব্যর্ত হয় তাহলে এটাই প্রমানিত হয় যে, সমাজে ভারসাম্য সৃষ্টর জন্যে এক চরমপন্থা নির্মূলে আরেক চরমপন্থারই প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে কুরআন শরীফে একটি ধারণা পাওয়া যায়:
“যদি আল্লাহ্ তায়ালা একটি জনগোষ্টী দিয়ে আরেকটি জনগোষ্টিকে প্রতিহত না করতেন তাহলে পৃথিবী বিপর্যস্ত হয়ে যেতো; কিন্তু আল্লাহ্ জগতসমূহের প্রতি অনুগ্রহশীল।” (২: ২৫১)
সুতরাং তরুণ মুসলমানদের প্রতি অভিযোগ অযৌক্তিক, যখন প্রতিপক্ষ চরমপন্থীরা ধর্ম ও নৈতিকতা বিগর্হিত জীবনের গড্ডালিকা প্রবাহে ভেসে যাচ্ছে। যেসব তরুণ ইসলামী শিক্ষা অনুযায়ী তাদের জীবন গড়ে তুলতে প্রয়াসী তাদেরকে হেয় করার প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ অযৌক্তক ও অন্যায়। যেসব তরুণ পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ছে, রোযা রাখছে, দাড়ি রাখছে, গিরার উপর কাপড় পরছে, হালাল হারাম বিবেচনা করছে, ধুমপান থেকে বিরত থাকছে তাদেরকে দোষ দেয়ার বা নিন্দা করার কী যুক্তি থাকতে পারে। অথচ আমরা নীরবে চোখের সামনে দেখি একদল লোক জীবনকে উপভোগ করে চলেছে নির্বিচারে। নৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক দিক দিয়ে পাশ্চাত্যের এই মানসপুত্ররা সম্পূর্ণ উচ্ছন্নে গেছে। অতএব ধর্মীয় “চরমপন্থার” বিরুদ্ধে “গেলো গেলো রব” তোলা আর “ধর্মহীন চরমপন্থা” র পক্ষে চোখ কান বুজে থাকা যুক্তির কোন্ মানদন্ডে সঙ্গত? মেয়েরা পর্দা করে চলাফেরা করলে উপহাসের পাত্রী হতে হয়; কিন্তু যখন আরেক দল মেয়ে রাস্তাঘাচে, সৈকতে, থিয়েটারে, সিনেমায় প্রায় উলঙ্গভাবে নিজেকে প্রদর্শন করে তখন তাকে “সংবিধানসম্মত ব্যক্তি স্বাধীনতা” ভোগ বলে পার পাওয়া কী উচিত? তাহলে কী ধরে নিতে হবে, সংবিধানে নগ্নতা ও বেহায়াপনার জন্যে ব্যক্তি স্বাধীনতার অনুমতি দেয়া হয়েছে, আর সতীত্ব ও শালীনতা নিষিদ্ধ করা হয়েছে? সমাজ যদি অনৈতিক ও ধর্মহীন তৎপরতা প্রতিরোধে এগিয়ে আসতো তাহলে আমাদের দেশে ধর্মীয় চরমপন্থা’র উদ্ভব হতো না, যদিও কোনো না কোনো কারণে চরমপন্থা বিরাজ করতে তাহলে এর প্রবাব হতো নগণ্য। আমাদের এটা স্বীকার করতে হবে ‘চরমপন্থা’ একটি বিশ্বজনীন ঘটনা; কিন্তু মজার ব্যাপার বিভিন্ন দেশে আন্যান্য চরমপন্থী গ্রুপ বা সংগঠন থাকলেও তাদের বিরুদ্ধে এ রকম চরম পদক্ষেপ নেয়া হয় না। কিন্তু যত দোষ কেবল মুসলমানদের বেলায়। তারা চরমপন্থী হলে তাদের বিরুদ্ধে নানা অজুহাতে চরম নির্যাতনের পথ বেছে নেয়া হয়। ইসরাঈলের চরমপন্থী ইহুদীরা মনে করে ঐ ভূমিতে তাদের ঈশী অধিকার রয়েছে এবং এই লক্ষ্যে তারা সকল রকম হিংস্র তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। অথচ খোদ ইসরাঈলের সৃষ্টিটাই অবৈধ এবং সন্ত্রাসী কাজ। লেবাননে খ্রীস্টান ফালাজির চরম সহিংস পন্থায় মুসলমানদের ওপর নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে। তারা মুসলমানদের যবাই করছে, তাদের লাশ ক্ষতবিক্ষত করছে, গুপ্ত অঙ্গ কেটে তাদেরই মুখে পুরে দিচ্ছে, মুসলমানদের ধর্মীয় বইপুস্তক পুড়িয়ে ফেলছে। খ্রীস্টানদের ধর্মীয় গ্রন্থে বলা হয়েছে, “তোমার শত্রুকে ভালবাসো, তোমাকে যারা ঘৃণাকরে তাদের ভাল করো, কেউ তোমার ডান গালে চড় মারলে বাম গালও পেতে দাও।” (লুক ৬ : ২৭-২৯)।
এছাড়া আমরা অন্যান্য দেশ, যেমন সাইপ্রাস, ফিলিপাইন ও হিন্দুস্থানে মুসলমানদের বিরুদ্ধে সন্তাসী তৎপরতা দেখতে পাই। মুসলমানদের বিরুদ্ধে এক সর্বাত্মক খ্রীস্টানী সন্ত্রাস শুরু হয়েছে যাকে বলা যায় নতুন ক্রুসেড। প্রতি বছর হিন্দু চরমপন্থীরা মুসলমানদের ওপর হত্যাযজ্ঞ চালাচ্ছে। পরিহাসের বিষয়, হিন্দুরা প্রাণী হত্যাকে নির্দয় নিষ্ঠুর কাজ বলে মনে করে। এ জন্যে তাদের ধর্মে গরু যবাই নিষিদ্ধ। কিন্তু এরাই আবার ঠাণ্ডা মাথায় মানুষ হত্যা করে চলেছে বেধড়ক! একই কারণে তারা আবাদী জমিতে নাকি কীটনাশক ব্যবহার করে না। লাখ লাখ একর জমির ফসল তাই ইঁদুরের পেটে চলে যায়। তাদের দৃষ্টিতে এসব প্রাণীরও আত্মা আছে, তাই তাদের আঘাত করা যাবে না। তাদের দৃষ্টিতে বোধ হয় একমাত্র মুসলমান নামক প্রাণীরই আত্মা নেই!
একথাও আমাদের স্বীকার করতে হবে, বস্তুবাদ মানুষের চিন্তাও আচরণকে বিকৃত করে ছেলেছে। বিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের চরম উন্নতি হয়েছে, মানুষ চাঁদেও গেছে, গ্রহান্তরে আধিপত্য বিস্তার করছে। কিন্তু এসব বৈষয়িক উন্নতির পাশাপাশি আত্মার উন্নতি হয়নি। বিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের চরম উন্নতি হয়েছে, মানুষ চাঁদেও গেছে, গ্রহান্তরে আধিপত্য বিস্তার করছে। কিন্তু এসব বৈষয়িক উন্নতির পাশাপাশি আত্মার উন্নতি হয়নি। ফলে মানুষ আজ মনের সুখ পাচ্ছে না। এক সমায় তারা মনে করেছিলো বস্তুগত আরাম-আয়েশ লাভ করতে পারলে মনের শান্তিও পাওয়া যাবে। কিন্তু তাদের সে আশার গুড়ে বালি! তাদের মধ্যে চরম নৈরাজ্য দেখা দিয়েছে। হিপ্পি জাতীয় নানা গ্রুপ নিত্য নতুন গজাচ্ছে তাদের কাছে আধুনিক সভ্যতা অর্থহীন হয়ে পড়েছে, তারা এখন প্রকৃতিতে ফিরে যেতে চায়। তাদের মনে প্রশ্ন জেগেছে : আমি কে? আমার লক্ষ্য কি? আমি কোথা থেকে এসেছি? এখন থেকে আমাকে কোথায় যেতে হবে? কিন্তু পাশ্চাত্যের কাছে এসব প্রশ্নের জবাব নেই। এমনি নৈরাজ্যের প্রতিধ্বনি আমাদের দেশেও শোনা যায় এই প্রশ্নের জবাব নেই। এই প্রশ্নের জবাব পেতে গিয়ে কেউ চরম বিধর্মি হয়ে গেছে, আবার কেউবা সত্য পথের সন্ধান পেয়ে ইসলামের সুশীতল চায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। সুখের বিষয়, বহু মুসলিম তরুণ সকল প্রশ্নের সছিক উত্তর ইসলামের মধৈই খুঁজে পেয়ে নিজেদের জীবনকে ইকামতে দ্বীনের জন্যে কুরবানী করতে প্রস্তুত।
আজকের বিশ্বে চারদিকে হিংসা আর বিদ্রোহের বহ্নি। এর মাঝে শান্তি, নমনীয়তা ও ভারসাম্য প্রত্যাশা করা অসঙ্গত। উৎসাহী তরুণদের কাছ থেকে মিরব্বীদের মতো প্রজ্ঞা ও পরিণত চিন্তা আশা করা যুক্তিসঙ্গত নয়। মানুষ প্রাথমিকভাবে পরিবেশেই সৃষ্টি। গুপ্ত পুলিশকে কঠোর ব্যবস্থা, নির্যাতন ও গুপ্ত হত্যা বন্ধ করতে হবে। স্বাধীনতা, সমালোচনা ও পারস্পরিক পরামর্শের অধিকার দিয়ে সুস্থ পরিবেশ সৃষ্টিতে উদ্যোগী হতে হবে। হযরত উমর (রা)-এর একটি কথায় আমরা এর নযীর পাই: “আল্লাহ্ তাদের রহম করুন যারা আমার ত্রুটিগুলো দেখিয়ে দেয়।” তাই তিনি তাকে পরামর্শ দানে ও তার সমালোচনা করতে সকলকে উৎসাহ দিতেন। একদিন এক ব্যাক্তি হযরত উমর (রা) কে বলেন, “হে খলীফা, আল্লাহ্ কে ভয় করুন!” উমর (রা)-এর সঙ্গীরা ত্রুদ্ধ হলেন। কিন্তু হযরত ওমর (রঅ) লোকটিকে নির্দ্বিধায় বলতে দিলেন এবং তাঁর সঙ্গীদেরকে বললেন, “তোমরা যদি (এই লোকটির মতো) কথা না বলো তাহলে তাতে কল্যাণ নেই এবং আমাদের (শাসকদের) মধ্যেও কোনো কল্যাণ নেই যদি আমরা তোমাদের (পরামর্শ ও সমালৌচনা) না শুনি।” আরেকবার উমর (রা) শ্রোতাদের উদ্দেশ্য বললেন, “তোমাদের মধ্যে বিচ্যুতি দেখে তাহলে আমকে সঠিক পথে আনার দায়িত্ব তারই।” এ কথা শুনে একজন লোক উঠে দাঁড়িয়ে বলল, “আল্লাহর শপথ, আপনার মধ্যে আমরা যদি আমার মধ্যে বিচ্যুতি দেখি তাহলে এই তোলয়ার দিয়ে আপনাকে ঠিক করব। (অথাৎ বল প্রয়োগ)।” উমর (রা) রাগ না খুশী হয়ে বললেন: “আলহ্মদুলিল্লাহ, মুসলমানরা তলোয়ার দিয়ে উমরকে ঠিক পথে আনার জন্যে তৈরি আছে।” বস্তুত স্বাধীন পরিবেশ থাকলে নানা মতের উদ্ভব ঘটে এবং সেগুলো নিয়ে সাধারণ মানুষসহ বিচক্ষণ ব্যাক্তিরা আলাপ-আলোচনা করে ভালটা গ্রহণ ও মন্দটা বর্জন করতে পারেন। ফলে অপ্রীতিকর মতভেদের আশাঙ্কাও তিরোহিত হয়।
অন্যথায় চরমপন্থী ভাবধারা গোপনে সুপ্ত বীজের মতো বাড়তে বাড়তে মহীরুহে পরিণত হয়। অবশেষে একদিন সহিংস তৎপরতার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়ে সকলকে হতবাক করে দেয়। মন ও মেধা চরমপন্থী চিন্তাধারার উৎস। এর মুকাবিলায়ও মন ও মেধা প্রয়োজন। শক্তি প্রয়োগ করে এর মুকবিলা করতে গিয়ে হিতে বিপরীত হয়। সতর্কতা, ধৈর্য ও বুদ্ধিবৃত্তিক কৌশল অবলম্বন করেই চরমপন্থী মনোভাব পাল্ঠাতে হবে। কিন্তু সাময়িক অভ্যুথ্থানের নেতৃবৃন্দ এখানেই ভুল করে বসেন। তারা তাদের গুপ্ত পুলিশ লেলিয়ে দিয়ে তাদের প্রতিপক্ষের ওপর নিষ্ঠুর কায়দায় নির্যাতন চালান। এতে তারা সাময়িক সাফল্য অর্জন করেন বটে, কিন্তু চরমপন্থা দমনে শেষতক চরমভাবে ব্যর্থ হন। কেননা একটা চরমপন্থা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে।
অতএব, এই পর্যায়ে আমাদের প্রথম কর্তব্য হচ্ছে বুদ্ধিদীপ্ত ফিকাহর ভিত্তিতে যুক্তিগ্রাহ ইসলামী জাগরণ সৃষ্টি করতে হবে। এই ফিকহ শুধু ছোটখাট বিষয় নয়, বরং অপরিহার্য দিকগুলোর প্রতি মনোযোগ দেবে এবং খন্ড ও অখন্ড, শাখা ও মূল, মূর্ত ও বিমূর্ত বিষয়গুলোর যথার্থ রূপভেদ ব্যাখ্যা করবে। এ ধরনের ফিকহর বিকাশ সহজ কাজ নয়। মানুষের ধ্যান-ধরণায় পরিবতর্ন তথা কোন্টি সঠিক, কোন্টি ভুলতা বিচারের মানসিকতা গড়ে তোলার জন্যে আন্তরিক প্রয়াস, পচন্ড ধৈর্য এবং আল্লাহ্ তায়ালার সাহায্য দরকার।
ক্ষমতাসীনরা মনে করে, রেডিও-টিভিকে কাজে লাগিয়ে তাদের ইচ্ছা মাফিক গণমানস পরিবর্তন করা সম্ভব। কিন্তু মানুষ এ ধরনের সরকারী প্রচার কৌশলে আস্থা আনতে পারে না। বিভিন্ন দেশের সরকার কিছু ওলামা ও বাগ্মীকে এই কাজে লাগানোর চেষ্টা করেছেন, বিশেষ করে বন্দীদের চিন্তাধারা পরিবর্তনের চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু সকল প্রচেষ্টা নিদুরুণভাবে ব্যর্থ হয়েছে। একমাত্র সরকারী প্রভাবমুক্ত হাক্কানী আলিমরাই এই অবস্থার পরিবর্তন করতে পারেন। এসব মুক্ত হাক্কানী আলিম তাদের জ্ঞানের মৌলিকতা ও গভীরতার জন্যে যুব সামাজ তথা সাধারণ মানুষের আস্থা ও শ্যদ্ধাভাজন। কিন্তু এ জন্যে সন্ত্রাসমুক্ত স্বাভাবিক পরিবেশ দরকার। মুক্ত ও গঠনমূলক আলোচনা, পারস্পরিক যোগাযোগ ও ভাবের আদান-প্রদানের মাধ্যমেই সঠিক চিন্তার বিকাশ ঘটা সম্ভব। আদেশ-নিষেধ জারি করে রাতারাতি মনের রূপান্তর সম্বব নয়।
এ প্রসঙ্গে আমি যে বিষয়টির উপর গুরুত্ব দিতে চাই তা হচ্ছে একটি বুদ্ধিবৃত্তিক সন্ত্রাসকে আরেকটি বুদ্ধিবৃত্তিক সন্ত্রাস দিয়ে মুকাবিলার বিপদ অথাৎ একগুয়েমির সাথে একগুয়েমি, গোঁড়ামির সাথে গোঁড়ামি এবং অপকর্মের সাথে অপকর্মের মুকাবিলা। উদাহরণস্বরূপ পরস্পরের বিরূদ্ধে কুফরীর অভিযোগের কথা উল্লেখ করা যায়। এর সপক্ষে একটি হাদীসের কথা বলা হয়, “যে ব্যক্তি একজন মুসলমানকে কাফির বলে সে নিজেই কুযফরী করে।” কোনো বিষয়ে ব্যাখ্যার ভুল, সন্দেহ বা ভূল সিদ্ধান্তের জন্যে একজন মুসলমানকে উক্ত হাদীসের আলোকে কাফির বলে অভিযুক্ত করা যায় না। হাদীস ও সাহাবীদের জীবন থেকে আমরা এর প্রমাণ পেতে পারি। হযরত আলী (রা) খারিজীদের কেবল নিন্দাই করেছেন কিন্তু কাফির বলেননি। খারিজীরা তাকে কাফির বলে ফতোয়া দিয়েছিল। তিনি তাদের নিয়তকে ভাল মনে করে তাদেরকে ইসলামের আওতার মধ্যেই রেখেছিলেন। তাই তাঁকে যখন জিজ্ঞেস করা হয়েছিল খারিজীরা কাফির কিনা তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছিলেন, তারা কুফরঅ থেকে বেঁচে গেছে, তারা অথীতে আমাদের ভাই ছিল, আজ তারা ভূল করেছে। এর অর্থ আলখাওয়ারিজকে কাফির বা মুরতানিন না বলে বাগী বলে গণ্য করা যায়। এই ক্ষত্রে বুগাতের তাৎপর্য দাঁড়ায় ভুল ব্যাখ্যা ভিত্তিতে যে ব্যক্তি ন্যায়পরায়ণ মুসলিম ইমামের আনুগত্য করে না। এ ধরনের বাগীদের বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিকভাবে যুদ্ধ করা সমীচীন নয়, বরং সকল পন্থায় তাদেরকে সংশোধনের উদ্যোগ নিতে হবে। যুদ্ধ করতে হবে। যুদ্ধ ক্ষেত্রে যদি তারা বিপর্যস্ত হয় তাহলে তাদের সাথে কর্কশ আচরণ-নির্যাতন করাও উচিত হবে না। কেননা তাদেরকে নির্মূল করা নয়, বরং ইসলামের আওতায় ফিরিয়ে আনাই সকল প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য। অতএব তাদেরকে মুসলমান হিসেবেই গণ্য করতে হবে।
হযরত আলী (রা)-এর আমলে মত প্রকাশের স্বাধীনতাও ছিল নজিরবিহীন, সে অবস্থায় পৌঁছতে অনান্য দেশকে আরো বহু শত্বাদী অপেক্ষা করতে হয়েছেল। আলখাওয়ারিজ হযরত আলী (রা)-এর আপোস মীমাংসা নাবচ করেছিল এই দাবীতে যে, ‘সিদ্ধান্ত কেবল আল্লাহ্রই’। আলী (রা) তাঁর স্বভাবসিদ্ধ কন্ঠে জবাব দিয়েছিলেন, “বাতিলের স্বার্থে এটা সত্যের বিকৃতি।”তাদের চরম বিরোধিতা সত্ত্বেও আলী (রা) বলিষ্ঠ ভাষায় জানিয়ে দিয়েছিলেন: “আমরা তোমাদেরকে মসজিদে নামায আদায়ে বাধা দেব না, গনমতের মাল থেকে বঞ্চিত করব না, তোমরা যুদ্ধ শুরু না করলে আমরা করব না।”আলী (রা) এমনিভাবে খারিজীদের অথাৎ বিরোধী দলকে সকল অধিকার দিয়েছিলেন অথচ তিনি জানতেন তারা পূর্ণরূপে প্রশিক্ষিত সশস্ত্র সৈন্য, যে কোনো মুহূর্তে অস্ত্র ধারণে সক্ষম।
এই প্রসঙ্গে আরেকটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। আলখাওয়ারিজকে (খারিজীদের) কাফির বলে চিহ্নিত না করা সম্পর্কে আলিমদেরও সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত ছিল, যদিও প্রামাণিক হাদীসে এরূপ লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ও তদেরকে হত্যা করার অনুমতি রয়েছে। এমাম শাওকানী ‘নায়লুল আওতারে’ লিখেছেন, অধিকাংশ সুন্নী ফকীহ মনে করেন, কালিমা পাঠ ও ইসলামের মূল আহকাম মেনে চলায় খারিজীরা মুসলমান। তারা অন্য মুসলমানকে কাফির বলে অভিহিত করে, তারা নিজেরাই নিজেদের ভুল ব্যাখ্যার ফাঁদে পড়ে। তাদের পাপ ঐ ভুলেরই পরিণতি। আল-খিতাবী বলেন যে, যতোক্ষণ তারা ইসলামের মূলনীতিগুলো মেনে চলে ততোক্ষণ তাদের কাফির বলা ডাবে না। তাদের সাথে আন্তঃবিবাহ, খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদি করা যেতে পারে বলে আলিমরা একমত হয়েছেন।
ইয়াদ বলেন, মুতাকাল্লিমুনদের জন্যে একটি এটি অত্যন্ত জটিল বিষয় ছিল। ফকীহ আবদুল হক এমাম আবু মা’লীকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছিলেন। তিনি একজন কাফিরকে এসলামের মধ্যে অথবা একজন মুসলমানকে এর আওতা থেকে বহিষ্কার করার মতো জটিল ধর্মীয় বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে অস্বীকার করেন। কাজী আবু বকর আল-বাকিল্লানীও এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে অপারগতা প্রকাশ করেন বলে তিনি জানান। তবে তিনি বলেন, আল-খাওয়ারিজ প্রকাশ্য কুফরী করেনি কিন্তু কুফরীর মতো কথাবার্তা বলেছে। আল-গাযালী (র) তার আত-তাফরিকাহ বাইনাল ইমাম ওয়াল জান্দাকাহ গ্রন্থে লিখেছেন, “কাউকে কাফির চিহ্নিত করার ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক হতে হবে। একজন মুসলমানের রক্তপাতের চেয়ে এক হাজার কাফিরের জীবন বাঁচানো অপেক্ষাকৃত কত মারাত্মক ভুল।”
ইবনে বাত্তাল (র) বলেছেন, অধিকাংশ আলিম আল-খাওয়ারিজকে ইসলামের আওতার বাইরে রাখেননি। নাওরাওয়ানের খারিজীদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়ে আলী (রা) বলেছেন যে, তারা কুফরী এড়িয়ে গেছে। বাত্তাল তাদেরকে বুগাত বলে বিবেচনা করা যায় বলে মত প্রকাশ করেন। আলিমরা এ ব্যাপারে একমত যে, তাকফীর (কাউকে কাফির বলে চিহ্নিত করা) এমন একটি মারাত্মক বিষয় যা মারাত্মক পরিণাম ডেকে আনতে পারে।মুসলিম মনীষীরা মূল প্রামাণিক সূত্র থেকে বিভিন্ন বিষয় সিদ্ধান্তে নেয়ার নির্দিষ্ট নীতি ও পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন। এ থেকে উসুল আল-ফিকাহ বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। বিজ্ঞানের এই অতুলনীয় শাখা ইসলামের প্রামাণিক সূত্র থেকে আইন প্রণয়নের পদ্ধতিগত ভিত্তি নির্মাণ করেছে। এ জন্যে মুসলমানরা গর্ববোধ করতে পারে। এছাড়া উসুল থেকে কোনো নীতি সূত্র পাওয়া না গেলে উসুল আত-তাফসীর ও উসুল আল-হাদীসে তার সন্ধান পাওয়া যেতেপারে। শারীয়াহ সম্পর্কে গভীর জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্য ঈমান, হাদীসের ব্যাখ্যা ও আইন সংক্রান্ত অসংখ্য বই পুস্তকের সাহায্যও নেয়া যেতে পারে।
অতএব জ্ঞানের এসব সূত্রের বিদ্যমানতায় কুরআনের আয়াত ও হাদীসের মর্ম গভীরভাবে উপলদ্ধি করার ক্ষেত্রে কোনো অসুবিধে থাকতে পারে না। অগভীর ভাসাভাসা জ্ঞানের কোনো অবকাশ নেই। এই লক্ষ্যে নিম্মোক্ত বিষয়গুলো অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে:
প্রথম: ইসলামের সার্বিক সত্যের প্রেক্ষিতে সকল বিশেষ বিশেষ দিক বিবেচনা ব্যতিরেকে শারীয়াহ সম্পর্কে গভীর জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি পরিপক্ক হতে পারে না। কুরআনের একটি আয়াত অথবা একটি হাদীস অবশ্যই ব্যাখ্যা করতে হবে অন্য আরেকটি হাদীস হাদীস, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সুন্নাহ, সাহাবীদের জীবন ও উসূল আত-তাফরীরে আলোকে। এছাড়া সার্বিক প্রেক্ষাপট ও শারীয়াহর উদ্দেশ্যকেও সামনে রাখতে হবে। অন্যথায় উপলব্ধি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ভ্রান্তির ফলে শরীয়তে পরস্পর বিরোধীতার আপদ দেখা দেবে। এ কারণে ইমাম আশ-শাতিবি (র) ইজতিহাদের ক্ষেত্রে দু’টি শর্ত আরোপ করেছেন: (ক) সামগ্রিক চৈতন্যে শরীয়ত অনুধাবন ও (খ) সেই উপলব্ধির আলোকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা। এই শর্ত পূরণের একমাত্র উপায় হচ্ছে কুরআনের ও হাদীসের গভীর জ্ঞান এবং সেই সাথে কারণ, ঘটনাবলী, পরিবেশ, পরিস্থিতি এবং প্রতিটি আয়াত ও হাদীসের উদ্দেশ্যে সম্পর্কে সম্যক অবহিত হতে হবে। এছাড়া চিরন্তন অপরিবর্তনীয় এবং সাময়িক চাহিদা পূরণ, প্রচলিত প্রথা ও ঐতিহ্য, বিশেষ বিশেষ সময়ের ঘটনাবলী এবং পরিবর্তিত অবস্থায় এসবের পরিবর্তন ইত্যাদির রূপভেদ নির্ণয়ের ক্ষমতা থাকতে হবে।
একদিন আমি মহিলাদের ইসলামী পোশাক সম্পর্কে বক্তৃতা করছিলাম। একজন শ্রোতা বললেন, কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী হিযাবের সাথে একটি অতিরিক্ত বহিরাবরণ থাকতে হবে। আমি জবাব দিলাম, হিযাব নিজেই একটি উদ্দেশ্য নয়, বরং শরীরের শরীয়ত নিষিদ্ধ অংশগুলো শালীনভাবে আবৃত করার উপায় মাত্র এই সময় ও স্থানভেদে এর ধরন বিভিন্ন রকম হতে পারে। কিন্তু লোকটি অগ্নিশর্মা হয়ে চিৎকার করে বলল, কুরআন শরীফে পোশাক সুস্পষ্টত নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। এটা পরিবর্তনের অধিকার আমাদের নেই বলে সে কুরআনের এই আয়াতটি তিলাওয়াত করলো:
“হে নবী! আপনার স্ত্রীগণ, কন্যাগণ ও ঈমানদারদের নারীদের বলুন, যেন তারা তাদের চাদরের কিয়দাংশ নিজেদের উপর টেনে দেয়। এতে তাদেরকে চেনা সহজতর হবে; ফলে তাদের উত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।” (৩৩:৫৯)
আমি বললাম, কুরআনুল করীমে কখনো কখনো ওহী নাযিলের সমসাময়িক অবস্থার দিকে লক্ষ্য রেখে উপায় ও পদ্ধতি বাতলে দেয়া হয়েছে। এর চেয়ে উত্তম বা অনুরূপ অন্য কোনো উপায় উদ্ভাবিত হলে ঐটাই স্থায়ীভাবে মানতে হবে এমন ধরা বাঁধা তাৎপর্য ঐ আয়াতে নিহিত নেই। এর পক্ষে নিম্মোক্ত উদাহরণটিই যথেষ্ট: কুরআনুল করীম বলছে: “তোমরা তাদের মোকাবিলার জন্য যথাসাধ্য শক্তি ও অশ্ববাহিনী প্রস্তুত রাখবে। এতদ্বারা তোমরা সন্ত্রস্ত করবে আল্লাহর শত্রুকে, তোমাদের শত্রুকে এবং এতদ্ব্যতীত অন্যদেরকে, যাদেরকে তোমরা জান না, আল।রাহ জানেন।” (৮:৬০)
এই আয়াত নাযিলের সময় ঘোড়া ছিল যুদ্ধের সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যমগুলোর মধ্যে অন্যতম। তাহলে এখন কি মুসলমানরা ট্যাংক, জঙ্গী বিমান, বোমা ইত্যাদি ব্যবহার করতে পারবে না? এটা যদি ঠিক না হয় তাহলে এই আলোকে মুসলিম মহিলারাও শ্লীলতার উদ্দেশ্য সামনে রেখে যে কোনো বহিরাবরণ ব্যবহার করতে পারে।
আল-হাদীসকেও একইভাবে মূল্যায়ন করা যায়। আল-হাদীস ও শিক্ষায় জীবনের নানা ক্ষেত্রের প্রণালী-প্রক্রিয়া বিধৃত হয়েছে যার কতকাংশ আইন এবং অনেকাংশ আইন নয়; কিছু সাধারণ, কিছু নির্দিষ্ট, কিছু অপরিবর্তনীয়, কিছু পরিবতর্নীয়।পানাহার, পোশাক ইত্যাদি ব্যাপারে নির্দিষ্ট আইন আছে। আবার নির্দিষ্ট আইন নয় এমন সুন্নাহ ও রীতি-প্রথাও রয়েছে। যেমন- চামচের পরিবর্তে হাত দিয়ে খাওয়া বাধ্যতামূলক নয়। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সময়ে হাত দিয়ে খাওয়া আরবদের সাধারণ জীবনযাত্রার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল। এর অর্থ এই নয় যে, চামচ ব্যবহার হারাম। কিন্তু সোনা- রূপোর তৈজসপত্র সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। একইভাবে ডান হাত ব্যবহারের অভিন্ন প্রথা প্রবর্তন এর উদ্দেশ্য। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, “বিসমিল্লাহ বলো (খাওয়ার আগে) এবং ডান হাত দিয়ে খাও।” (অনুমোদিত হাদীস) আরেকটি হাদীসে তিনি বলেন, “তোমাদের বাম হাতে পানাহার করা উচিত নয়। কারণ শয়তান বাম হাতে পানাহার করে।” (মুসলিম)
রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সময় চালুনি সম্পর্কে কোনো ধারনা ছিল না। তাই বলে এটার ব্যবহার এখন বিদআত হতে পারে না।
অনেক তরূণ খাট ইজার বা ছওব পরিধানকে ইসলামের মৌলিক বিষয় মনে করে। তাদের প্রথম যুক্তি রাসূলুল্লাহ (সা) ও তাঁর সাহাবারা এটা পরিধান করেছিলেন। দ্বিতীয়ত হাদীসে গোড়ালির নিচে পর্যন্ত ইজার বা ছওব পরা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। হাদীসটি হচ্ছে: “গোড়ালির নিচে ইজার পরিধানকারী ব্যাক্তি দোযখে যাবে।” (বুখারী)
প্রথম যুক্তিটির ব্যাপারে বলা যায়, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সুন্নাহ সম্পর্কে আমরা যা জেনেছি তাতে দেখা যায় তিনি যখন যেমন পেয়েছেন তেমনিই পরেছেন। তাকে কোর্তা, ঢিলে জামা এবং এজারও পরতে দেখা গেছে। তিনি এয়েমেন ও পারস্য থেকে প্রাপ্ত (কিনারে সিল্কের নক্শা করা) কাপড়ও পরেছেন। পাগড়ি ছাড়া বা পাগড়[ইসহ টুপিও পরেছেন।
ইমাম ইবনূল কাইয়েম (র) তাঁর আল-হাদী আন-নববী বইয়ে লিখেছেন: পোশাক সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সর্বোত্তম রীতি তাই যা তিনি নিজে ব্যবহার করেছেন, করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং উৎসাহিত করেছেন।-তিনি উয়েমেনের পোশাক, সবুজ কাপড় চোপড়, জুব্বাহ, ফুলহাতা জামা এবং জুতা-স্যান্ডেলও পরেছেন। তিনি কখনো কখনো বাবরিও রেখেছেন।
তখন বস্ত্রকল অজ্ঞাত ছিল। ইয়েমেন, মিসর ও সিরিয়া থেকে কাপড় আমদানী করা হতো। এখন আমরা বিভিন্ন ধরনের অর্ন্তবাস ব্যবহার করি। তখন তা ছিল না। অতএব এসব নিয়ে অহেতুক শোরগোল কেন?
দ্বিতীয়: কুফফারের অনুকরণ সংক্রান্ত যুক্তি প্রশ্ন বলা যায়, আমাদেরকে আসলে কুফফারদের (অন্য ধর্মের অনুসারীদের) বৈশিষ্ট্য অনুসরণে নিষেধ করা হয়েছে; যেমন-ক্রস, ধর্মীয় পরিচ্ছদ, দর্মীয় আচার-সিরাত আল-মুসতাকিম মুখলিফাত আহলিল জাহীম” পুস্তকে এগুলোর বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। এখন একজন মুসলমান যদি ইচ্ছাকৃত কুফফারকে অনুসরণ করে তবে তা দোষনীয়। কিন্তু কেউ যদি অনিচ্ছাকৃতভাবে প্রয়োজনের তাকিদে করে তবে তা দোষনীয়। যেমন কোনো ফ্যক্টরী শ্রমিক বা ইঞ্জিনিয়ার কাজের সুবিধার্থে “ওভারঅল” পরলে দৌষের যথাসম্ভব নিজেস্ব বৈশিষ।ট্য ফুটিয়ে তোলা উচিত। সারকথা, খাটো ছওব পরা বাঞ্ছনীয়, কিন্তু ঔদ্ধত্যের পরিচায়ক না হলে লম্বা কাপড় পরা নিষিদ্ধ নয়।
উপরের উদাহরণগুলো নির্ভেজাল ব্যাক্তিগত ব্যাপার। অথচ আমরা বৃহত্তর জাতীয়, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক জটিল বিষয়গোলো নিয়ে এতো মাথা ঘামাই না যদিও তা গোটা উম্মাকে হুমকির মুখে ঠেলে দৈয়া এসব সমস্যা সমাধানে বরং আমাদেরকে ইসলামী আইনের গভিরে প্রবেশ করা উচিত।
আমাদের এটা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, এখন আমরা এক জটিলতম জগতে বাস করছি। নানা মত ও আদর্শের নজিরবীহিন প্রসারের ফলে পৃথিবী ছোট হয়ে এসেছে। সমাজে দুর্বল-শক্তিশালী, মহিলা-পুরুষ, সৎ ও সীমালংঘকারী ইত্যাদি রয়েছে। অতএব ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা পুনরুজ্জাঈবনের আন্দলনের প্রতি মানুষকে আহবান জানানো এবং কোনো বিষয়ে ফতোয়া দেয়ার সময় এই জটিল প্রেক্ষাপট বিবেচনা করতে হবে। আল্লাহর রেজামন্দি প্রত্যাশী একজন মুসলমান ব্যক্তি জীবনে চরমপন্থী মত পোষণ কিংবা কঠোর নিয়মশৃখলার মনে চলতে পারে। গান-ব্দ্য, নাটক এসবের স্থান তার জীবন নেই। কিন্তু কোনো আধুনিক রাষ্ট্র টিভি, রেডিও, আলোকচিত্র, সংবাদপত্র বা সংবাদ মাধ্যম ছাড়া চলতে পারে না। ইমিগ্রেশন, পাসপোর্ট, ট্রিফিক, শিক্ষা ও আইন শৃংখলার ক্ষেত্রে ছবি এখন অপরিহার্য। অপরাধ ও জালিয়াতি প্রতিরোধে এর ব্যবহার এখন ব্যাপক ও অত্যাবশ্যক। অতএব আধুনিক কোনো রাষ্ট্র ও সমাজ কি টিভির গুরুত্ব অস্বীকার করতে পারে? অথচ ফটোভিত্তিক বলে অনেকে এটাকে হারাম বলে মনে করেন।
সংক্ষেপে আমি যা বলতে চাই, নিছক ব্যক্তি জীবনে কড়াকড়ি সহনীয়; কিন্তু সমাজ বা রাষ্ট্রের উপর তা চাপিয়ে দেয়াএ চিন্তা অবাস্তব। একানে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাদীসটি আবার স্মতূব্য: “যে নামাযের ইমামতি করে তার উচিত নামায সংক্ষিপ্ত করা। কেননা জামাতে দুর্বল, বৃদ্ধ এবং ব্যস্ত লোকও থাকে।” (বুখারী)
একটি মারাত্মক সমস্যা হচ্ছে, আমাদের মধ্যে অনেকে এটা স্বীকার করতে চান না যে, শরীয়তের সকল আহ্কাম সমভাবে গুরুত্বপূর্ণ নয়। আহ্কামের বিভিন্ন ব্যাখ্যা থাকতে পারে এটাও তারা মানতে চান না। প্রথা, আচার-আচরণ ও দৈনন্দিন লেনদেনের ক্ষেত্রে অনেক বিষয় আনুমানিক সিদ্ধান্তের উপর নির্ভরশীল। এগুলো ইজতিহাদ সাপেক্ষ এবং স?ঠিক ইজতিহাদ থেকে উৎসারিত সিদ্ধান্তবলীতে মতানৈক্য ক্ষতিকর নয়, বরং এটি শরীয়তে নমনীয়ত ও ফিকাহর ব্যাপকতার প্রমাণ এবং উম্মার জন্যে আশীর্বাদ। এসব বিষয় সাহাবায়ে কিরাম (রা) এবং তাদের উত্তরর্সরীদের মধ্যেও মতভেদ ছিল। কিন্তু এগুলো কখনোই তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে পারেনি। অন্যদিকে ঈমান ও ইবাদত সম্পর্কিত আহকাম কুরআন ও সুন্নাহতে সুস্পষ্ট ও সুনির্ধারিত। এটা মুসলিম উম্মার মানসিক ও আচরণগত ঐক্যের প্রতীক। এগুলো থেকে বিচ্যূতি শুধু পাপ নয়, একজনকে কুফরীর দিকেও ঠেলে দিতে পারে। এছাড়া আরো কিছু আহকাম আছে যেগুলো প্রত্যাখ্যান করা আল্লাহ ও রাসূলকে অস্বীকার করার নামান্তর। পক্ষান্তের এমন সব বিষয় আছে যেগুলো ব্যাখ্যা নিয়ে ফকীহরা মতভেদ করেছেন। যেমন, কেউ বাধ্য হয়ে একজন মুসলমানকে হত্যা করলে, হত্যাকারী, না যে হত্যা করালো, কে শাস্তি পাবে? না-কি উভয়ে শাস্তি ভোগ করবে? এই জটিল প্রশ্নের বিভিন্ন মিজহাবের ফীকহ বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কেবল ইমাম আহমদ (র)-এর হাম্বলী মাজহাবেই এ ব্যাপারে এতো মতভেদ রয়েছে যে, তারা এ নিয়ে ১২ খন্ডের বই লিখেছেন। বইটির নাম: আল-ইনসাফ ফীর রাজিহ মিনাল ইখতিলাফ।
এই প্রেক্ষিতে মুসলিম তরুণদেরকে মতানৈক্য ও মতৈক্যের বিষয়গুলো এবং মতানৈক্য নিরসনের মনদন্ড সম্পর্কে অবহিত হতে হবে। এই লক্ষ্যে আমাদের আলিম ও উলামার কাছ থেকে প্রাপ্ত মতভেদ নীতি বা আদাব আল-ইখতিলাফের সাথে পরিচিত হওয়া আবশ্যক। তাহলে আমরা বিভিন্ন ধর্মীয় বিষয়ে উদার ও পরমতসহিষ্ণু হওয়ার শিক্ষা লঅভ করতে পারব। ভ্রাতৃত্ব বজায় রেখেও আমরা কিভাবে মতভেদ করতে পারি? প্রথমেই আমাদের উপলব্ধি করতে হবে, প্রান্তিক বিষয়ে মতনৈক্য স্বাভাবিক। সুস্পষ্ট আহকাম ও অস্পষ্ট আহকাম সৃষ্টির পেছনেও ঐশী প্রজ্ঞা রয়েছে। অস্পষ্ট আহকাম ও বিভিন্নমুখী হওয়া সত্ত্বেও এর মধ্যে ভ্রাতৃত্বসুলভ মতভেদেরও সম্ভ।আবনা থাকে। এটাও আল্লাহ্ তায়ালার আর্শীবাদ, বিশেষ করে সেই সব আলিমের উপর যারা মজহাব নির্বিশেষে একটি বিষয়ের সকল দিক বিচার বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম। এরূপ বিশিষ্ট আয়েম্মোর সারিতে যারা রয়েছেন তাঁদের কয়েকজনের নাম উল্লেখযোগ্য: উবনে দাকীক আল ঈদ, ইবনে তাইমিয়া, ইবনুল কাইয়েম, ইবনে কাছীর, ইবনে হাজার আল আছকালানী, আল দাহলাবী, আশ-শাওকানী, আল-সানানী (র) বলতেন: “আমি কখনোই কামনা করিনি যে, সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে মতনৈক্য না থাক। তাদের মতনৈক্য রহমতস্বরূপ।”
এমনকি রাসূলুল্লাহ্ (সা) -এর জীবদ্দশায়ও একটি বিষয়ের বিভিন্ন ব্যাখ্যা পাওয়া যেতো। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এগুলো অনুমোদন করতেন এবং তিনি ব্যক্তি বিশেষ বা গ্রুপকে দোষী বলে চিহ্নিত করতেন না। জঙ্গে আহযাবের পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবীদের উদ্দেশ্যে বললেন: “যে ব্যক্তি আল্লাহ ও কিয়ামত দিবসে বিশ্বাস করে সে যেন বানু কুরাইজায় (বসতা) না পৌঁছা পর্যন্ত সালাতুল আসর আদায় না করে।” (বুখারী ও মুসলিম) কতিপয় সাহাবী এটাকে অসম্ভব মনে করে গন্তব্যে পৌঁছার আগেই সালাত আদায় করে নিলেন। অন্যরা অর্থাৎ আক্ষরিক অর্থ গ্রহণকারীরা বানু কুরাইজার পৌঁছে নামায পড়লেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে এটা জানানো হল, তিনি উভয় পক্ষের কাজ অনুমোদন করলেন যদিও একপক্ষ ভুল করেছিল। এ থেকে আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারি, নিরেট প্রমাণের ভিত্তিতে প্রণীত ব্যাখ্যাকেই মেনে চললে তাতে পাপ হওয়ার কোনো আশঙ্কা নেই।
দুভার্গজনকভাবে আজকার একদল লোক আছেন যারা দাবী করেন তারাই সকল সত্যের আধার এবং সব প্রশ্নের জবাব তাদের কাছেই আছে এবং অন্যের উপর তা চাপি’য়ে দদিতে চান। তারা মনে করে তারা সকল মাযহাব ও মতভেদ নির্মূল করে এক আঘাতেই সকলকে একই প্লাটফর্মে হাযির করতে সক্ষম। তারা এ কথা বেমালুম ভুলে যান যে তাদের সিদ্ধান্তটাও অনুমান নির্ভর এবং তা ভুল বা শুদ্ধ উভয়ই হতে পারে। মোটকথা কোনো মানুষ অথবা কোনো আলিম অভ্রান্ত নন। একমাত্র নিশ্চিত ব্যাপার হচ্ছে, তার ইজতিহাদের জন্যে তিনি পুরস্কার পাবেন ভুল বা শুদ্ধ যাই হোক। অবশ্য তার নিয়ত সৎ থাকতে হবে। সুতরাং উপরোল্লিখিত ব্যক্তিরা একটা অতিরিক্ত মাহযাব সৃষ্টি ছাড়া আর কিছুই আশা করত পারেন না! এটা অদ্ভুত যে, তারা মাহযাবের অনুসৃতি অনুমোদন করেন না, কিন্তু অন্যকে নিজেদের নতুন মাহযাব অনুসরণে প্রলুবাধ করেন। তারা চান তাদের সৃষ্ট ‘একমাত্র’ মাহযাব সকলেই মেনে নিক। একবার এই ‘একমাত্র’ মাহযাবের একজন অনুসারী আমাকে জিজ্ঞেস করলেন: কেন সকল মুসলমান একটি মাত্র ফিকহী মতের অনুসারী হতে পারেন না? আমি জবাবে বললাম যে, মৌলসূত্রের ভিত্তিতে সকলের ঐকমত্য চাই। তা হতে হবে প্রামাণিক, অভিন্ন ও নির্বিরোধ এবং সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য। এর বিরোধিতায় আর কোনো মৌলসূত্র উথ্থাপিত হতে পারবে না এবং পূর্বোল্লিখিত তিনটি বিষয়ে সকল আয়েম্মায়ে হাদীসের মতৈক্য থাকতে হবে। সংক্ষেপে, এই বিষয়ে ইমাম ইবনে তাইমিয়া (র)-এর “রাফআল মালাম আনিল আয়েম্মাইল আলাম,শাহ ওয়ালীউল্লঅহ দেহলভীর হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ ও আল-ইনসাফ ফী আসবাবিল ইখতিলাফ এবং শেখ আলী আল-খলীফার আসবাব ইখতিলাফীল ফুকাহা” গ্রন্থে যেসব শর্তের উল্লেখ করা হয়েছে তা পূরণ করতে হবে। এখন আসুন আমরা নিচের হাদীসগুলো পর্যালোচনা করি:
১. যে নারী সোনার হার পরবে তাকে কিয়াতমের দিনে অনুরূপ একটি আগুনের তৈরি হার পরানো হবে এবং যে নারী সোনার দুল পরবে তাকে কিয়ামতের দিন অনুরূপ একটি আগুনের তৈরি দুল পরানো হবে। (আবু দাউদ, নাসায়ী)
২. কেউ যদি তার প্রিয়জনকে কিয়ামতের দিন আগুনের দুল পরাতে চায় তবে সে যেন তাকে সোনার দুল পরেত দেয় এবং কেউ যদি তার প্রিয়জনকে কিয়ামতের দিন আগুনের বালা পরাতে চায় সে যেন তাকে সোনার বালা পরতে দেয়। কিন্তু তোমারা পছন্দ মতো রূপা ব্যবহার করতে পারো। (আবু দাউদ)
৩.ছওবান (রা) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর কন্যা ফাতিমাকে (রা) সোনার চেন পরার জন্যে হুঁশিয়ার করে দিয়েছিলেন। এতে সাড়া দিয়ে তিনি সেটা বিক্রি করে একটি গোলাম খরিদ করলেন এবং তাকে আযাদ করে দিলেন। যখন রাসূলুল্লাহ (সা)-কে এ কথা জানানো হলো তখন তিনি বললেন, আলহামদু লিল্লাহ! তিনি ফাতিমাকে আগুন থেকে বাঁচিয়ে নিলেন।
ফকীহরা এসব হাদীস সম্পর্কে বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন: কেউ কেউ এগুলোর এনসান (হাদীসের বর্ণনা সূত্র) দূর্বল বলে প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং নিষিদ্ধ করার জন্যে অপর্যাপ্ত বিবেচনা করেছেন। কেউ কেউ ইসনাদকে সঠিক বললেও অন্য সূত্র থেকে প্রমাণ করেছেন যে, মেয়েরা সোনার অলংকার ব্যবহার করতে পারে। আর-বায়হাকী ও অনান্য ফকীহ এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন বলে লিখেছেন এবং একে স্বীকৃত প্রচলন বলে ফিকায় মেনে নেয়া হয়েছে।
অন্য ফকীহরা অন্য হাদীসের ভিত্তিতে, যারা মজুদ সোনার যাকাত আদায় করেননি, তাদের ক্ষেত্রে এই হাদীস প্রযোজ্য বলে রায় দিয়েছেন। এই অন্য হাদীসগুলো আবার সমালোচনার উর্ধ্ব নয়। আবার, মহিলাদের গহণার যাকাত সম্পর্কেও বিভিন্ন মাযহাবে মতভেদ রয়েছে।
কেউ কেউ আবার যুক্তি দেখিয়েছেন, যেসব মহিলা অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে অহংকারবশত সোনার অলঙ্কার পরে এই হাদীসে তাদেরকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। আন নাসাঈ এই বিষয়ের সাথে সংগতিপূর্ণ কতিপয় হাদীস উল্লেখ করে “বাবুল কারাহিয়াহ লি নিসা এজার আলহালি জাহাব” শীষর্ক পস্তুক রচনা করেছেন। অনান্য ফকীহ বলেছেন, অহংকারবশত অতিরিক্ত সোনা ব্যবহার প্রশ্নের হাদীস জড়িত।
আধুনিক কালে শেখ নাসিরুদ্দীন আর-আলবানী (র) গত ১৪শত বছরেএ সকল মাযহাবের রায় বাতিল করে দিয়ে বলেছেন, হাদীসগুলোর ইসনাদ শুধু প্রমাণিকই নয়, এগুলো অন্য হাদীস দ্বারা বাতিলও হয়নি। সুতরাং গলার হার ও কানের দুল পরা নিষিদ্দ।
অতএব মতনৈক্যের যে দুর্বার স্রোত এগিয়ে চলছে তা কি বালির বাধ দিয়ে রুখা সম্ভব? প্রশ্নের জবাব অতি পরিষ্কার: “মতাভেদের অসংখ্য স্রোতধারা প্রবাহিত হতেই থাকবে, কিন্তু তা আমাদেরকে নিসজ্জিত করতে পারেবে না ইনশাআল্লাহ।” আল্লাহ্ তায়ালা বলেন: “প্রত্যেকেরই একটা দিক আছে, যার দিকে সে মুখ করে দাঁড়ায়।” (২:১৪৮)
এ প্রসঙ্গে আমি বলতে চাই আধুনিক কালে একজন মাত্র ধর্মীয় নেতা মতভেদের নীতি ও তাৎপর্য গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি ইমাম হাসান আল-বান্না (র)। মুসলিম উম্মাহর সংগতি লক্ষ্যে নিবেদিত হয়েও তিনি তার অনুসারীদের এর নূন্যতম মর্ম উপলব্ধি করাতে পেরেছিলৈন এবং ইসলামী নীতিমালার ভিত্তিতে ঐক্যমত সৃষ্টি তাদেরকে এক প্লাটফর্মে সমবেত করার নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তিনি মতভেদের অনিবার্যতা সম্পর্কে স্থির নিশ্চিত হয়েছিলেন। তার বিখ্যাত উসুল আল-ইশরুন গ্রন্থ থেকে এটা সুস্পষ্ট হয়। এ বিষয়টি তিনি দক্ষতার সাথে তার বিভিন্ন বাণীতে তুলে ধরেছেন। ‘আমাদের দাওয়াত’ শীষর্ক বাণীতে তিনি বলেন যে, তার আহবান সর্বসাধারণের প্রতি, কোনো বিশেষ গ্রুপের প্রতি নয় এবং কোনো বিশেষ চিন্তাধারার প্রতিও নয়। দ্বীনের প্রকৃত মর্ম উপলব্ধি করাই আমাদের কাম্যঅ এজন্যে বৃহত্তর কল্যাণে সকল প্রচেষ্টা সম্মিলিত খাতে প্রবাহিত করাই আমাদের লক্ষ্য। আমরা মতৈক্য চাই, খামখেয়ালী নয়। কারণ সকল দুর্ভাগ্যের জন্যে দায়ী ভ্রান্তিপূর্ণ মতভেদ। আমরা বিশ্বাস করি বিজয় অর্জনের জন্যে ভালবাসা একটি বড় উপাদান অতএব ব্যার্থতার দিকে টেনে নিয়ে যেতে পারে এমন বিষয় পরিহার করাই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু এ সত্ত্বেও তিনি লিখেছেন:
“নানা কারণে ছোটখাট ধর্মীয় বিষয়ে মতভেদ অনিবার্য। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারনগুলো হচ্ছে বুদ্ধিবৃত্তির মাত্রা ও জ্হানের গভীরতার তারতম্য, বহুবিদ বাস্তব ঘটনা ও থথ্যের পারস্পারিক সম্পর্কে এবং ভাষায় অন্তর্নিহিত দ্ব্যর্থতা। এসব কারণে মূলসূত্রের ব্যাখ্যার বিভিন্নতার দরুন মতভেদের উদ্ভব অপরিহার্য।
ইসলামী বিশ্বের কোনো অংশে জ্ঞানের উৎসের প্রাচুর্য আবার অনান্য জায়গায় দুষ্পাপ্যতাও একটি বড় কারণ। এমাম মালিক (র) আবু জাফরকে (র) বলেন, “রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাহাবীরা বিভিন্ন দূরবর্তী অঞ্চলে ছড়িয়েপড়েছিলেন, প্রত্যেকের কাছে জ্হান সঞ্চিত ছিল। তুমি যদি একটিমত অনুসরণে জবরদস্তি করো তাহলে ফিতনা সৃষ্টি করবে।”
পরিবেশগত পার্থকও রয়েছে। ইমাম শাফিঈ (র) ইরাক ও মিসরের বিরাজমান অবস্থার প্রেক্ষিতে ভিন্ন ভিন্ন ফতোয়া দিতেন। উভয় ক্ষেত্রে তিনি যা সত্য বলে রা’বীর প্রতি ইমামের দৃষ্টিভঙ্গি মতপার্থক্যের আরেকটি কারণ। একজন রা’বীকে একজন এমাম নির্ভরযোগ্য বিবেচনা করেন, আরেকজন তাতে সংশয় প্রকাশ করেন।
এসব কারণে আমরা বিশ্বাস করি, ধর্মীয় গৌণ বিষয়ে সর্বসম্মত মত অসম্ভব নয়, দ্বীনের প্রকৃতির সাথে অসংতিপূর্ণ। কেননা এরূপ দাবী কঠোরতা ও বাড়াবাড়ি জন্ম দেবে। আর এটা ইসলামের সরলতা, নমনীয়তা ও উদারতার পরিপন্থী। নিঃসন্দেহে এই মূল্যবোধগুলোর কারণেই ইসলাম যুগের দাবী মেটাতে সক্ষম।
অধিকন্তু, যেহেতুঋ আমরা সকলে ইসলামের সুবিস্তৃত কাঠিমোর আওতাধীন তাই গৌণ বিষয়ে মতভেদ আমাদের পারস্পারিক ভালবাসা ও সহযোগিতাকে ক্ষুণ্ণ করতে পারে না। আমরা যদি মুসলমান হই তাহলে আমরা কি মুসলমান ভাইদের পোষণ করে যাওয়ার সম্ভাব্য প্রীতিপূর্ণ পরিবেশ গড়তে পারি না? অন্তত এ প্রশ্নে তো একমত হতে পারি।
রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাহাবীরা ফতোয়ায় মতভেদ পোষণ করেছেন কিন্তু তা অনৈক্য সৃষ্টি করেনি। সালাহ ও বনু কুরাইজার ঘটনাটি এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। তারা আমাদের চেয়ে ভালভাবে জানা সত্ত্বেও যদি মতভেদ করে থাকেন তাহলে এটা কি অবাঞ্ছিত নয় যে, আমরা তুচ্ছ ব্যাপারে বিদ্বেষবশত মতনৈক্যে লিপ্ত হই? যদি আমাদের ইমামগণ বিভিন্ন বিষয়ে মতদ্বৈততা পোষণ করেন তাহলে আমাদেরও তা হতে পারে। যদি প্রাত্যহিক আযানের মতো প্রতিষ্ঠিত গৌণ বিষয়ে মতবিরোধ থাকতে পারে তাহলে অন্যান্য জটিল বিষয়ের কি দৃশ্য হবে?
আমাদেরকে এটাও স্মরণ রাখতে হয় যে, খিলাফত আমলে বিরোধীয় বিষয়গুলো খলিফার কাছে পেশ করা হতো। এখন যেহেতু খলীফা নেই সেহেতু এমন নির্ভরযোগ্য সূত্র বা ব্যক্তিত্ব খুঁজতে হবে যেন সেখানে বিরোধপূর্ণ বিষয়গুলো সমাধান করা যায়; নতুবা মতবিরোধ আরেকটি মতবিরোধের জন্ম দবে। পরিশেষে,আমাদের ভ্রাতাগণ এসব বিষয়ে পূর্ণ সচেতন এবং তাদের মধ্যে সহিষ্ণুতা ও উদারতা থাকা আবশ্যক। তারা বিশ্বাস করেন প্রতিটি গ্রুপের দাওয়াতের মধ্যে কিছু সত্য, কিছু মিথ্যা উপাদান থাকতে পারে। তারা সতর্ক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর সত্যকে গ্রহণ করেন এবং যারা ভুল উপলব্ধি করেন, তাহলে খুব ভালো, আর যদি না করেন তবুও তাঁরা আমেদর মুসলিম ভাই। আমরা আল্লাহর কাছে সঠিক পথের দিশা চাই!”
ফিকাহর মতভেদ সংক্রান্ত একটি ঘটনার উল্লেখ করতে চাই। রমযান মাসে একদিন তিনি মিসরের একটি ছোট গ্রামে বক্তৃতার দাওয়াত পান। সেকানে দু’দল লোক তারাবীর নামাযের সংখ্যা নিয়ে বাকবিতণ্ডা করছিল। একদল বলল, উমর ইবনে খাত্তাব (রা)-এর দৃষ্টান্ত অনুযায়ী ২০ রাকাত। আরেক দল ৮ রাকাতের উপর জোর দিচ্ছিল। তাদের যুক্তি ছিল রাসূলুল্লাহ (সা) কখনো আট রাকাতের বেশি তারাবীহ পড়েননি। উভয় পক্ষ একে অপরকে বিদাতের অভিযোগে অভিযুক্ত করল। পরিস্থিতি এক পর্যায়ে হাতাহাতির উপক্রম হলো। তারা আল-বান্না (র)-এর কাছে বিষয়টি পেশ করল। তিনি প্রথম প্রশ্ন করলেন: তারাবীহ কী ধরনের ধর্মীয় অনুষ্ঠান? জবাব এলো: সুন্নাত, পালন করলে সওয়াব, না করলে গুনাহ। অতঃপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন: মুসলিম ভ্রাতৃত্ব সম্পর্কে কী মত? তারা জবাব দিল: বাধ্যতামূলক এবং ঈমানের অন্যতম মৌলিক বিষয়। কখন আল-বান্না (র) বললেন: তাহলে শরীয়তের দ্রষ্টিতে ফরয অথবা সুন্নতের মধ্যে কোন্টি পরিত্যাগ করা যুক্তিযুক্ত? অতঃপর তিনি বললেন: আপনারা যদি ভ্রাতৃত্ব ও ঐক্য চান তাহলে প্রতিটি বাড়িতে গিয়ে নিজেদের বিশ্বাস মোতাবেক তারাবীহর নামায পড়ুন। তর্ক করার চেয়ে এটাই উত্তম।
ঘটনাটি আমি কিছু লোকের কাছে বর্ণনা করলে তারা বললেন, আল-বান্নার পদক্ষেপ সত্য এড়িয়ে যাওয়ার শামিল। তিনি সুন্নাত ও বিদাতের পার্থক্য নিরূপণ করেননি। আমি বললাম, এ বিষয়ে মত বিরোধের অবকাশ আছে। আমি নিজে যদিও তারাবীহর নামায আট রাকাত পড়ি, কিন্তু যারা বিশ রাকাত পড়ে তাদেরকে বিদাতীর দায়ে অভিযুক্ত করি না। তারা অনমনীয়তা ব্যক্ত করে বলল, এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দেয়া মুসলমানদের কর্তব্য। আমি যুক্তি দেখালাম, এটা হালাল ও হারামের ব্যাপারে সত্য; কিন্তু ফিকহী মাসলার ক্ষেত্রে নয়। সেখানে বিভিন্ন বিষয়ে মতভেদ আছে, অতএব প্রত্যেক পছন্দ অনুযায়ী একটি মত বেছে নিতে পারেন, কিন্তু এ ব্যাপারে গোঁড়ামি অনাবশ্যক।
অনেক বিজ্ঞ আলিম এটি স্বীকার করেছেন। হাম্বালী কিতাব ‘শারহে গায়াত আল-মুনতাহা’য় বলা হয়েছে:
কেউ যখন ইজতিহাদী সিদ্ধান্ত নাকচ করে তখন সে মুজতাহিদুনের মর্যাদা সম্পর্কে অজ্ঞতাবশত এরূপ করে, যাদেরকে আল্লাহ্ ভুল বা শুদ্ধ পরিশ্রম সাপেক্ষ সিদ্ধান্তের জন্যে পুরস্কৃত করবেন। তাদেরকে অনুসরণ গুণাহ হবে না। কেনা তারা যে ইজতিহাদে পৌঁছেছেন তা আল্লাহ্র নির্ধারিত পথ ধরেই এগিয়েছে; ফলে তা শরীয়তের অংশ হয়ে যায়। একটি উদাহরণ, প্রয়োজনে মৃত প্রাণীর গোশত খাওয়ার অনুমতি আছে, কিন্তু ইচ্ছাকৃত খাওয়া নিষিদ্ধ। দুটোই সুপ্রতিষ্ঠিত ফিকহী সিদ্ধান্ত।
ইমাম ইবনে তাইমিয়া (র) তাঁর ‘আল-ফাতাওয়াল মিসরীয়া’ বইয়ে বলেছেন, ঐক্যের কথা বিবেচনা করাই সঠিক পথ। অবশ্য সম্প্রতীতি ও সখ্যতা সৃষ্টির লক্ষ্যে পছন্দনীয় জিনিস পরিহার করাও সংগত। যেমন রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত ইবরাহীম (আ)-এর স্থাপিত ভিত্তির উপর কা’বা নির্মাণ পরিত্যাগ করেছিলেন*। ইমাম আহমদ (র)-এর মতো ইমামগণ ঐক্য রক্ষার স্বার্থে পছন্দনীয় বিষয় পরিহার করে মতৈক্যের বিষয় মেনে নেয়ার পক্ষপাতী।
ইবনে তাইমিয়া ৯র) কা’বা নির্মাণ সংক্রান্ত নিম্মোক্ত হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত আয়েশা (রা)-কে বলেন: তোমাদের জনসাধারণ সম্প্রতি যদি জিহিলিয়ার মধ্রে না থাকতো তআহলে আমি (হযরত) ইবারাহীম (আ)-এর ভিত্তির উপর কা’বা পুনঃনির্মাণ করতাম। ইবনুল কাইয়েম সালাতুল ফজরে কুনুতের বিষয়টিও তুলেছেন। কেউ এটাকে বিদাত বলেন আর কেউ এটা দুর্দিনে আমল করার পক্ষে। তিনি তাঁর বই ‘যাদুল মাদে’ বলেছেন, আপকালে এটা আমল করা রাসূলের সুন্নাত। হাদীস বিশারদরাও এটা সুন্নাত জেনে আমল করেছেন; আর যারা এটাকে রাসূলের সুন্নাত বলে জানতে পারেননি তারা এটাকে আমল করেননি। ইবনুল কাইয়েম লিখেছেন: “নামাযে রুকু থেকে ওঠার পর আল্লাহর রহমত কামনা ও তাঁর শুকরিয়া আদায়ের উপযুক্ত মুহূর্ত।”
রাসূলুল্লাহ (সা) এই অবস্থায় দু’টি কাজেই করেছেন। এ সময় ইমামের সশব্দে দোয়া পাঠ গ্রহণযোগ্য যাতে মোক্তাদিরা শুনতে পায়। উমর ইবনে খাত্তাব (রা) ও ইবনে আব্বাস (রা) ও এরূপ করতেন যাতে মানুষ সুন্নাহ জানতে পারে। উমর ইবনে খাত্তাব (রা) শব্দে সূরা ফাতিহা তিলাওয়াত করতেন এবং ইবনে আব্বাস (রা) জানাযার নামাযেও এরূপ করতেন। এগুলো গ্রহণযোগ্য মতভেদ সাপেক্ষ কাজ। যারা এরূপ করেন বা যারা করেন না কেউই দোষণীয় নন। যেমন নামাযে হাত তোলা, কিরান ও তামাত্তুর বিভিন্ন প্রক্রিয়া।
আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে রাসূলের সুন্নাত তুলে ধরা। কোন্টি জায়েয, কোন্টি নাজায়েয তা চিহ্নিত করার চেষ্টা আমি করিনি, বরং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সর্বোৎকৃষ্ট সুন্নাত তুলে ধরাই আমার উদ্দেশ্যঅ আমরা যদি বলি রাসূলুল্লাহ (সা)-নেই, তার অর্থ এই নয় যে, তিনি অন্যকে ও ব্যাপারে নিয়মিত করতে বলেছেন কিংবা কেউ পালন করলে তা রিদ্দাহর পর্যায়ভুক্ত হবে।
এক মাযহাবের অনুসারী অন্য মাযহাবের ইমামের পেছনে নামাযও আদায় করতে পারে; যদিও ঐ মুক্তাদি মনে করে যে, এতে তার মাযহাবে তা সিদ্ধ। এবনে তাইমিয়াহ (র) ‘আল-ফাওয়াকিহুল আদিদাহ’ পুস্তকে লিখেছেন: সাহাবায়ে কিরাম, তাবিঈন এবং চার ইমামের রীতি অনুসারে পরস্পরের পেছনে নামায পড়া সিদ্ধ বলে মুসলমানরা সর্বসম্মত। যে এটাকে অগ্রাহ করে সে বিপথে চালিত মুবতাদী এবং কুরআন ও সুন্নাহর শিক্ষা ও সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত থেকে বিছু্যত হয়।
কোনো কোনো সাহাবী ও তাবিঈন জোরে বাসমালাহ উচ্চারণ করেছেন, কিন্তু অন্যরা করেননি, এতদসত্ত্বেও তারা পরস্পরের পেছনে নামায আদায় করে?ছেন। আবু হানিফা (র) ও তার অনুসারীরাও তাই করেছেন। শাফিঈরা মদীনায় মালিকীদের পেছনে নামায পড়তেছিলেন। কারণ, ইমাম মালিক (র) ফতোয়া দিয়েছিলেন এই অবস্থায় নতুন করে অযু করার দররকার নেই।
অবশ্য ইমাম আহমদ আবনে হাম্বল (র) শরীর বা নাক থেকে রক্ষক্ষরণহলে অবশ্যই গোসর করতে হবে বলে মত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু কোন মুসল্লী যদি ইমামের শরীর থেকে রক্তক্ষরণ হতে দেখে তাহলে তার পেছনে সে নামায গড়ে যাবে কিনা এ প্রশ্নে ইমাম হাম্বাল (র) বলেন: “সাঈদ আবনে মুসাইয়াবের ও মালিকের (র) পেছনে নামায না পড়া অচিন্ত্যনীয়। অতঃপর তিনি দু’টো বিবেচ্য বিষয়ের উপর আলোকপাত করেছেন:
(ক) ইমামের কোনো আচরণ সালাতকে বাতিল করলেও তা যদি মোক্তাদির দৃষ্টি এড়ায় তাহলে মোক্তাদিকে নামায চালিয়ে যেতে হবে। এ ব্যাপারে পূর্ববর্তী ওলামা ও চার ইমাম একমত। (খ) কিন্তু ইমাম নাপাক হতে পারেন এমন কিছু যদি করেন আর সে ব্যাপারে মোক্তাদি যদি নিশ্চিত হয় তবে সে তার মর্জি মাফিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে। কেননা এ ব্যাপারে ব্যাপক মোনৈক্য রয়েছে। আমাদের পূর্ববর্তী বুযর্গদের মতে এরূপ ইমামের পেছনে নামায পড়া জায়েয। মালিকী মাযহাবও তাই মনে করে; কিন্তু শাফিঈ ও আবু হানিফা (র) ভিন্ন মত পোষণ করেন। আহমদের বিভিন্ন বক্তব্য থেকে এই মতের প্রতিই সমর্থন পাওয়া যায়। (আল ফাওয়াকিহ আলাআদিদা; কারাজাতি, ফতোয়া মুয়াসিরাহ।)
২. জ্ঞান, মূল্যবোধ ও কর্ম
শরীয়তী কাজ ও কর্তব্যের মূল্য উপলব্ধিতে ফিকাহর জ্ঞান সহায়ক ভূমিকা পালন করে। আর আদেশ ও নিষেধের মানদন্ডে এসব কাজ ও কর্তব্যের সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এই জ্হান বিবিধ ও সাদৃশ্যের মধ্যেকার বিভ্রান্তি প্রতিরোধ করে। জীবনের ওপর ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রভাবের আলোকে ইসলাম প্রতিটি কর্মের মূল্যমান নির্ধারণ করে দিয়েছে।
মুস্তাহাব (প্রশংসনীয়) কাজগুলো না করলে শাস্তি নেই, কিন্তু করলে পুরস্কার আছে। আবার এমন বিষয় আছে যা রাসূলুল্লাহ (সা) সর্বদা করেছেন, পরিহার করেননি; কিন্তু অন্যকে করার জন্যে সুস্পষ্ট আদেশ দেননি। এগুলো যে বাধ্যতামূলক নয় তা প্রমাণ করার সাহাবায়ে কিরাম এসব কাজের কিছু কিছু করেননি। মাযহাবগুলোর মত অনুযায়ী মুস্তাহাবের আদেশ আছে; কিন্তু সুস্পষ্টভাবে নয়। ফরয দ্বর্থহীনভাবে বাধ্যতামূলক, করলে সওয়াব, উপেক্ষা করলে গুনাহ। আর পালন না করলে ফিস্ক, পাপকার্য। আর বিশ্বাস না করলে কুফরী। ফরয দু’ভাগে বিভক্ত। ফরযে কিফায়াহ (সমষ্টিক কর্তব্য) ও ফরযে আইন (ব্যাক্তিগত কর্তব্য)। ব্যাক্তিগত কর্তব্য প্রত্যেক মুসলমানকে পালন করতে হবে। আর সমষ্টিক কর্তব্য কেউ করলেই চলবে, অন্যরা না করলে গুনাহ নেই। ব্যাক্তিগত কর্তব্যের শ্রেণী বিভাগ আছে। এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ফারাইয যা ঈমানের মৌলিক অঙ্গ, যেমন শাহাদাহ অথাৎ সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মা’বুদ নেই এবং হযরত মুহাম্মদ মোন্তোফা (সা) তাঁর রাসূল এবং কর্মে প্রতিফলন হচ্ছে সালাত, যাকাত, সিয়াম ও হজ্জের মাধ্যমে। আরো কম গুরুত্বপূর্ণ ফারাইয আছে, কিন্তু এগুলোও বাধ্যতামূলক। ফরযে কিফায়ার চেয়ে ফরযে আইনের গুরুত্ব অধিক। পিতার প্রতি সদাচার ফরযে আইন যা জিহাদের চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ, জিহাদ ফরযে কিফায়াহ। পিতার অনুমতি ছাড়া পুত্র জিহাদে অংশ নিতে পারবে না। এ সম্পর্কে প্রামাণিক হাদীস আছে। আবার ব্যাক্তিগত অধিকারের সাথে সংশ্লিষ্ট ফরযে আইনের ওপর সামাজিক অধিকারের সাথে সম্পৃক্ত ফরযে কিফায়াহ অগ্রাধিকার পাবে। মুসলিম ভূখন্ড আক্রান্ত হলে জিহাদ ফরযে আইন। তখন পিতার অধিকার গৌণ হয়ে যায়। এমনিভাবে ওয়াজিবের ওপর ফরয, সুন্নাতের ওপর ওয়াজিব ও মুস্তাহাবের ওপর সুন্নাতের অগ্রাধিকার রয়েছে। একইভাবে ইসলাম ব্যাক্তিগত আত্মীয়তার ওপর সামাজিক দায়িত্ব এবং এক ব্যাক্তির জন্যে উপকারী কাজের ওপর একাধিক ব্যক্তির উপকার হতে পারে এমন কাজে অগ্রাধিকার দেয়। নফল এবাদত, দান খয়রাতের চেয়ে দু’পক্ষের মধ্যেকার বিরোধ মীমাংসার প্রতিও ইবাদত ইসলাম অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে। একজন শাসককে তার নফল ইবাদতের চেয়ে তার সুবিচারের জন্যে বেশি পুরস্কার দেয়া হবে। অবক্ষয়ের যুগে মুসলমানরা যেসব ভুল করেছিলো সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিচে দেয়া হলো:
১. তারা উম্মার স্বাসংশ্লিষ্ট বৈজ্হানিক শিল্প ও সামরিক ক্ষেত্রে উদ্ভাবন ও উৎকর্ষ অর্জনের প্রচেষ্ঠা উপেক্ষা করেছে। এছাড়া ইজতিহাদ, আহকাম ও দাওয়া এবং স্বৈরশাসনের বিরোধিতা উপেক্ষা করেছে।
২. তারা ভাল কাজের আদেশ ও খারাপ কাজের নিষেধের মতো ব্যাক্তিগত কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করেনি।
৩.তারা কোনো মৌল বিশ্বাসকে কম গুরুত্ব দিয়ে অপর একটিকে বেশি পালন করেছে। তারা রমযানের নামাযের চেয়ে অগ্রাধিকার দিয়েছে। অজন্যে নামাযীর চেয়ে রোযাদারের সংখ্যা বেশি দেখা গেছে, বিশেষ করে মহিলাদের ক্ষেত্রে। এদের মধ্যে আবার কেউ কখনো সিজদাই করেনি। অনেকে যাকাতের চেয়েসালাতের বেশি গুরুত্ব দিয়েছে যদিও আল্লাহ তায়ালা কুরআনে একত্রে বাইশ বার এ দু’টো কাজের আদেশ দিয়েছেন। এজন্যে সাহাবায়ে কিরাম বলতেন, “যাকাত ছাড়া সালাত বাতিল।” আর হযরত আবু বকর (রা) তো যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন।
৪. পরযসমূহ ও ওয়াজিবাতের চেয়ে নাওয়াফিলের প্রতি বেশি গুরুত্ব দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে সূফীদের দৃষ্টান্ত উল্লেখযোগ্য। তারা নানা আচার-অনুষ্ঠান, যিকর ও তাসবীহর ওপর মনোযোগ দিয়েছেন; সামাজিক ও রাজনৈতিক অনাচার প্রতিরোধের মতো সামাজিক দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসেননি।
৫. তারা জিহাদ,ফিকাহ, আপোস-মীমাংসা, সৎকর্মে সহযোগিতা ইত্যাদির মতো সামাজিক দায়িত্ব অগ্রাহ করে ব্যাক্তিগত ইবাদত-বন্দেগীতে ব্যস্ত থেকেছেন।
৬. শেষত, অধিকাংশ মানুষ ঈমান, তাওহীদ, নৈতিক উৎকর্ষের মাধ্যমে আল্লাহর রেজামন্দি হাসিল ইত্যাদি মৌলিক বিষয় বাদ দিয়ে গৌণ বিষয়ে ওপর অযথা গুরুত্ব দিয়েছেন।
নিষিদ্ধ বিষয়গুলোরও শ্রেণীভেদআছে: যেমন, মাকরূহাত (ঘৃণা) কিন্তু গুনাহ নেই। যেগুলো ঘৃণা কিন্তু স্পষ্টবাবে নিষিদ্ধ নয়, এসব হালালের চেয়ে হারামের কাছাকাছি। মুতাশবিহাত (অস্পষ্ট বা নিগূঢ়) সেগুলোই যা অল্প লোকের কাছে জ্ঞাত এবং অজ্ঞতাবশত করে ফেলা হয়। এগুলো হারাম। সুস্পষ্ট নিষিদ্ধ বিষয়গুলো কুরআন ও সুন্নায় বিস্তারিত বণূনা করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন, “তোমরা কেন খাও না (গোশত) যাতে আল্লাহর নাম উচ্চারিত হয়েছে যখন তিনি নিষিদ্ধ বিষয়গুলো বিস্তারিত ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন?” (৬:১১৯)
এই নিষেধাজ্হা দু’ভাগে বিভক্ত: ছোট ও বড়। ছোট বিষয়গুলো অপসৃত হয় সালাত, সিয়াম ও দান-খয়রাতের মাধ্যমে। কুরআনুল করীম থেকে আমরা জানি, “সুকৃতি দুষ্কৃতিকে অপরিসারিত করে।” (১১:১১৪)
রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সুন্নাত থেকে আমরা জানি, নিয়মিত সালাত ও সিয়াম আদায় করলে এরন মাঝখানের ছোট
ছোট গুনাহ মাফ হয়ে যায়। অবশ্য বড় পাপ কেবল খালেস তওবার মাধ্যমে মাফ হতে পারে। এর মধ্যে সবচেয়ে কবীরা গুনাহ হচ্ছে শিরক-আল্লাহর সাথে অন্য সত্তাকে শরীক করা। এ গুনাহর কখনো মাফ নেই। আল্লাহ বলেন: “আল্লাহ্ তাঁর সাথে শরীক করার অপরাধ মাফ করেন না, এছাড়া অনান্য অপরাধ যাকে ইচ্ছে মাফ করে দেন, যে কেউ আল্লাহ্র সাথে শরীক করে সে এক মহাপাপ করে।” (৪:৪৮)
অতঃপর হাদীসে উল্লেখিত পাপগুলো হচ্ছে: পিতামাতার অবাধ্যতা, মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া, যাদু, খুন, সুদ, এতীমের সম্পদ আত্মসাৎ এবং মিথ্যা সাক্ষ্য করে সতী মুসলিম মহিলাদের বিরুদ্ধে যিনার অপবাদ।
নিম্মোক্ত বিষয়গুলো থেকে ত্রুটি ও বিভ্রান্তি দেখা দেয়:
ক. মানুষের মধ্যে মুহাররামাতের চেয়ে মাকরূহাত ও মুতাশাবিহাতের প্রতি বাধা দেয়ার প্রবণতা বেশি দেখা যায়। অন্যদিকে ওয়াজিবাতকে উপেক্ষা করা হয়। সুস্পষ্ট হারামের পরিবর্তে মতভেদের বিষয়গুলো নিয়ে বেশি ব্যগ্রতা।
খ. অনেক লোক ভাগ্য গণনা, যাদু, মাযারকে নামাযের স্থান হিসেবে ব্যবহার, মৃতদের উদ্দেশ্য পশু উৎসর্গ, মৃতদের কাছ থেকে সাহায্য প্রার্থনা ইত্যাদি কবীরা গুনাহর পরিবর্তে ছগীরা গুনাহ প্রতিরোধে বেশি ব্যস্ত। অথচ কবীরা গুনাহগুলো তাওহীদী চেতনাকে দূষিত করে।
একইভাবে বিভিন্ন মুসলমানের আচরণও বিভিন্ন। কোনো কোনো ধার্মিক যুবক জ্ঞান, ঈমান ও শক্তির ব্যাপারে অন্য সকলকে এমন চোখে দেখে যেন তারা সবাই সমান। সুতরাং তারা সাধারণ ও জ্ঞানী-গুণী মানুষের মধ্যেও পার্থক্য করতে পারে না। এছাড়া পুরানো মুসলমান ও ন্ওমুসলিম এবং প্রাকৃতিক ভিন্নতার দিকে লক্ষ্য রেখেই শ্রমসাধ্য ও সহজবোধ্য, ফারাইয ও নাওয়াফিল, বাধ্যতামূলক ও ঐচ্ছিক অধিকারী করলাম আমার বান্দদের মধ্যে তাদেরকে যাদেরবে আমি মনোনীত করেছি; তবে তাদের মধ্যে কেউ নিজের ওপর যুলুম করে, কেউ মধ্যপন্থী এবং কেউ আল্লাহর ইচ্ছায় কল্যাণকর কাজে অগ্রগামী। এটাই মহাঅনুগ্রহ।” (৩৫: ৩২)
এ প্রসঙ্গে ‘যে ব্যাক্তি ভুল করেছে’ বলতে ‘যে নিষিদ্ধ কাজ এড়িয়ে গেছে এবং ‘যার ফরয কর্তব্য পালন অসম্পূর্ণ’ বোঝানো হয়েছে। ‘যে ব্যক্তি মধ্যমপন্থা অনুসরণ করে’ বলতে ‘যে কেবল অবশ্য পালনীয় কাজ সম্পন্ন করে এবং নিষেধাজ্ঞা পরিহার করে’ এমন ব্যক্তিকে বোঝানো হয়েছে। যে ব্যক্তি সৎকর্মে অত্যন্ত অগ্রণী বলতে ‘যে ব্যক্তি বাধ্যতামূলক ্ও অনুমোদিত কর্তব্য পালন করে এবং নিষিদ্ধ কাজ’ কেবল পরিহার করে না সকল ধরনের বাজে ও নিন্দনীয় কাজ থেকে বিনত থাকে এমন ব্যক্তিকে বোঝানো হয়েছে। উপরিউক্ত ধরনের সকল লোকই ইসলামী উম্মাহর অর্ন্তভুক্ত যাদেরকে আল্লাহ্ কিতাব দিয়েছেন। এই দৃষ্টিতে কেউ ভুল করলেই তাকে ফিসকের অভিযোগে অভিযুক্ত করা ঠিক হবে না অথবা মতভেদ আছে এমন আমল দেখলেই তাকে হারাম ফতোয়া দেয়াও যুক্তিযুক্ত নয়। যেসব তরুণ মুসলমান এরূপ তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে তাদের এ কথা ভুললে চলবে না যে, কুরআন স্পষ্টভাবে ছোট ও বড় গুনাহর পার্থক্য রেখা টেনে দিয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন:
“আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা আল্লাহর। যারা খারাপ কাজ করে তাদেকে তিনি দেন মন্দ ফল আর যারা ভাল কাজ করে তাদেরকে দেন উত্তমপুরস্কার, তারাই বিরত থাকে গুরুতর পাপ ও অশ্লীল কাজ থেকে, ছোটখাট অপরাধ করলেও। তোমার প্রতিপালকের ক্ষমা অপরিসীম।” (৫৩:৩১-৩২)
ছোটখাট ত্রুটির প্রতি সহনীয় দৃষ্টভঙ্গির ব্যাখ্যা একটি আরবী শব্দ ‘লামাম’-এ (ছোট ত্রুটি) পাওয়া যায়। লামামের দু’টি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্যা আছে।্আল-হাফিজ ইবনে কাছির (র) সূরা আন-নিসার ২৫৫-২৫৬ নং আয়াতের ব্যাখ্যা দিতে বলেছেন: ‘আলমুহসিমুনন’ শব্দের ব্যাখ্যা হচ্ছে যারা কবীরা গুনাহ ও লজ্জাকর কাজ পরিহার করে অথাৎ বড় বড় নিষিদ্ধ কাজ পরিত্যাগ করে। এরূপ লোক যদি ছোটখাট ভুল করে বসে, আল্লাহ্ তাকে মাফ করবেন এবং রক্ষা করবেন; যেমন তিনি আরেকটি আয়াতে ওয়াদা করেছেন:
“তোমাদেরকে যা নিষেধ করা হয়েছে তার মধ্রে যা গুরুতর তা হতে বিরত খাকলে তোমাদের লঘু পাপগুলো মোচন করব এবং তোমাদেরকে সম্মানজনক স্থানে দাখিল করব।” (৪:৩১)
তিনি আরো বলেন, “...যারা কবীরা গুনাহ ও লজ্জাকর কাজ পরিহার করে, কেবল ছোটখাট ভুল (করে)” এখানে ছোটখাট ত্রুটিকে (লামাম) সম্পূর্ণ বাদ দেয়া হয়েছে, কেননা এগুলো ছগীরা গুনাহ ও লজ্জাকর কাজের উপ-শ্রেণীভুক্ত।
ইবনে কাছির (র)-এর পরে বলেছেন: ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আবু হুরায়রাহ (রা) থেকে নিম্মোক্ত হাদীস শোনার পরেই কেবল লামেমের (ছোট খাট ত্রুটি) বিষয়টি আমি উপলব্ধি করেছি: ‘আল্লাহ্ পাক আদমের পুত্রের (মানুষ) জন্যে ব্যভিচারের অংশ নির্দিষ্ট করে রেখেছেন যা সে অনিবার্যভাবেই করবে। চোখের যিনা হচ্ছে একদৃষ্টে সেই বস্তু দেখা যা নিষিদ্ধ করা হয়েছে; জিহবার যিনা হচ্ছে উচ্চারণ; অন্তরে কামনা-বাসনার উদ্ভব এবং গোপন অংগের মাধ্যমে যার আস্বাদন অথবা প্রত্যাখ্যান।”
তাই আবু মাসউদ (রা) ও আবু হুরায়রাহ (রা) বলেন, “লামামমের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে: ‘স্থির দৃষ্টিতে তাকানো, চোখের ইশারা, চুম্বন এবং প্রকৃতপক্ষে ব্যভিচার করা ছাড়াই যৌন সঙ্গমের নিকটবতর্তী হওয়া।”
লামামের অন্য ব্যাখ্যাও ইবনে আব্বাস (রা) দিয়েছেন: লজ্জাকর কাজ বটে কিন্তু এর জন্যে অনুতপ্ত হয়। তিনি পদ্যাকারে একটি হাদীসের উদ্ধৃত দেন যার রূপান্তর করলে দাঁড়ায়, “হে আল্লাহ, আপনার ক্ষমা সীমাহীন, কেননা আপনার বান্দাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে ছোটখাট ভুল করে না।” (ইবনে কাছির)
আবু হুরায়রাহ (রা) ও আল হাসান (রা) যুক্তি দেখান: গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা না করেই যে ভুল করা হয় তাই লামাম এবং যা ঘন ঘন করা হয় না। উপরিউক্ত আলোচনার তাৎপর্য দাঁড়ায়: যারা নিয়মিত কবীরা গুনাহ করে না তাদের জন্যে ইসলামের অঙ্গন বিস্তৃত; কেননা যারা অনুতপ্ত তাদের জন্যে আল্লাহর দয়া প্রশস্ত।
যারা নিয়মিত ফরয কাজ আদায় করে, তাদের নগণ্য ভুলগুলোকে উপেক্ষা করা যায় কিভাবে, তার একটি শিক্ষণীয় দৃষ্টন্ত উমর ইবনে খাত্তাব (রা)-এর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পাওয়া যায়। বর্ণিত হয়েছে, আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) যখন মিসরে ছিলেন তখন তার কাছে কিছু লোক গিয়ে বললো, অনেকেই আলকুরআনের শিক্ষা মেনে চলছে না এবং তারা এ ব্যাপারে খলীফা উমর (রা) তখন তাদেরকে মদীনায় উমর (রা)-এর কাছে নিয়ে গেলেন এবং সফরের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করলেন। উমর (রা) তখন ঐ লোকেদের সাথে একটি বৈঠকের ব্যবস্থা করতে বললেন। বৈঠকে তার নিকটতম লোকটিকে উমর (রা) ব/ররেন, “সত্যি করে বলো, তুমি কি গোটা কুরআন পড়েছে?” লোকটি ইতিবাচক জবাব দিল। তারপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, “তুমি নিজে কি এর শিক্ষা কড়াকড়িভাবে মেনে চলো যেন তোমার হৃদয় ও কাজকর্ম পরিশুদ্ধ হয়?” লোকটি প্রতিটির জবাবে নেতিবাচক জবাব দিলো। উমর (রা) তখন বললেন, “তুমি কি (নিষিদ্ধ বিষয় ও বস্তুর) দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকানোর ব্যাপারে, মুখে উচ্চারণ ও বস্তুর জীবনের আচরণে এ রশিক্ষাগুলো কড়াকড়িভাবে মেনে চলেছ?” লোকটি প্রতিটির জবাবে নেতিবাচক জবাব দিলো। উমর (রা) তখন গ্রুপের প্রত্যেকলোককে এই প্রশ্ন করলে প্রত্যেকে নেতিবাচক জবাব দিল।
এরপর উমর (রা) বললেন, “তাহলে তোমরা কি করে খলীফার কাছে দাবী করতে পার যে, তোমরা যেভাবে আল্লাহর কিতাবকে বুঝেছ তাই মানুষকে মানতে বাধ্য করি যা তোমরা নিজেরাই করতে ব্যর্থ হয়েছ বলে স্বীকার করলে? আমাদের প্রভু জানেন যে, আমরা প্রত্যেকে কিছু না কিছু খারাপ কাজ করে ফেলি।” অতঃপর তিনি কুরআনের এই আয়াতটি পাঠ করলেন, “তোমরা যদি জঘন্যতম কাজগুলো থেকে বিরত থাকো তাহলে আমি তোমাদের সকল খারাপ কাজকে বিদূরিত করবো এবং মহান মর্যাদার তোরণে তোমাদের প্রবেশ করাবো।” (৪:৩১)
লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে উমর (রা) বললেন, “মদীনার বাসিন্দারা কি জানে তোমরা কি জন্যে একানে এসেছ?” তারা নেতিবাচক জবাব দিলে তিনি বললেন, “তারা যদি জানত তাহলে তোমাদেরকে আমি (শাস্তি দিয়ে) দৃষ্টান্ত বানাতাম।” (ইবনে কাছীর)
কুরআনুল করীমের গভীর জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে উমর (রা) তাৎক্ষণিকভাবে সরেজমিনে বিষয়টির নিষ্পত্তি করে দিলেন এবং এভাবে অহঙ্কারও গোঁড়ামির গোড়া কেটে দিলেন। এ ব্যাপারে তিনি যদি এতোটুকু দুর্বলতা দেখাতেন তাহলে সুদূরপ্রসারী মারাত্মক ফিতনা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠার আশঙ্কা ছিলো।
৩. অন্যের প্রতি সহৃদয় অনুভূতি
ব্যক্তিগতভাবে মানুষের ক্ষমতার তারতম্য এবং জীবনের রূঢ় বাস্তবতার বিভিন্ন স্তর থাকে। অন্তর্দৃষ্টি ও ফিকহের জ্ঞানের পাশাপাশি অন্যের এই বাস্তবতার প্রতিও পরস্পরের সহৃদয় অনুভূতি থাকা আবশ্যক। আন্দোলনের ক্ষেত্রে সকলের কাছ থেক হযরত হামযাহ ইবনে আবদুল মুত্তালিবের (রা) মতো শাহাদাতের শৌর্য প্রত্যাশা করা ঠিক হবে না। এটি এমন মহৎ গুণ, গভীরতম নিষ্ঠা ও অধ্যাবসায় ছাড়া যার প্রকৃত মর্ম খুব কম লোকই অনুধাবন করতে পারে।
কেউ কেউ শান্তভাবে সত্যের পক্ষে কথা বলে তৃপ্তিবোধ করে; অন্যেরা তাদের ধারনণা অনুযায়ী বিরাজমান মারাত্মক অবস্থার প্রেক্ষিতে নীরব থাকই নিরাপদ মনে করে। আবার অনেকে মনে করেন আগা নয়, গোড়া থেক সংস্কার কাজ চালাতে হবে। এজন্যে তারা ব্যাক্তি বিশেষের প্রতি তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। তারা মনে করে, এসব লোকের দৃষ্টিভঙ্গি সংস্কৃত ও পরিশুদ্ধ করতে পারলে কাঙ্খিত পরিবর্তন আসতে পারে। কিন্তু এটা বলাবাহুল্য, পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী ধর্মনিরপেক্ষ ব্যবস্থা নির্মূল করতে হলে সুনির্দিষ্ট ও দীর্ঘমেয়াদী কর্মসূচীর ভিত্তিতে একটি ইসলামী সঙগঠনের নেতৃত্বে সম্মলিত সংগ্রাম ছাড়া গত্যন্তর নেই। অবশ্য শরীয়ত এক মুন্কার থেকে যেন আরেকটি বড় মুনকারের সৃষ্টি না হয় সেজন্যে অনেক ক্ষেত্রে নীরবতাকে যুক্তিযুক্ত মনে করে। এ প্রসঙ্গে কুরআনুল করীমে হযরত মূসার (আ)-এর ঘটনা থেকে শিক্ষা পাওয়া যায়। মূসা (আ:) -কে তার স্থলাভিষুক্ত করে যান। কিন্তু তিনি চলে যাওয়ার পরপরই ইসরাঈলীরা সামেরিদের পরামর্শে একটি সোনার গো-মূর্তি বানিয়ে পূজো করতে শুরু করে। এই বিচ্যুতির বিরুদ্ধে হারুন (আ)-এর বক্তব্য শুনতেও তারা অস্বীকার করে। কুর্আন বলছে:
“হারুন তাদেরকে আগেই বলেছিলেন, হে আমার স্বজাতি! তোমাদেরকে এর দ্বারা পরীক্ষায় ফেলা হয়েছে। তোমাদের দয়াময়; সুতরাং তোমরা আমাকে অনুসরণ কর এবং আমার আদেশ মেনে চল। তারা বলেছিলো: আমাদের কাছে মূসা ফিরে না আসা পর্যন্ত আমরা পূজা হতে কিছুতেই বিরত হব না।” (২০:৯০-৯১)
তাদের অনমনীয়তা দেখে হারুন (আ) নিশ্চুপ হয়ে গেলেন। মূসা (আ) ফিরে এসে ক্রোধে ও দুঃখে অগ্নিশর্মা হয়ে হারুন (আ)-কে রূঢ়ভাবে তিরস্কার করলেন। কুরআনের বর্ণনা, “মুসা বলল, ও হারুন! তুমি যখন দেখলে তারা পথভ্রষ্ট হয়েছ তখন কিসে তোমাকে নিবৃত্ত করল- আমার অনুসরণ করা হতে? তবে কি তুমি আমার আদেশ অমান্য করলে!” (২০:৯২-৯৩)
হারুন (আ) জবাব দিলেন : “হে আমার সাহোদর! আমার দাড়ি ও চুল ধরে টেনে না; আমি আশংকা করেছিলাম যে, তুমি বলবে, তুমি বনী ইসরাঈলেদের মধ্যে বিভদ সৃষ্টি করেছে এবং তুমি বলবে, তুমি আমার কথা পালনে যত্নবান হওনি।” (২০ : ৯৪) সুতরাং দেখা যাচ্ছে সামাজি ঐক্য ও সম্প্রীতির স্বার্থে হারুন (আ) হযরত মূসা (আ) ফিরে না আসা পর্যন্ত নীরবতা অবলম্বন করেছেন। এই ঘটনার সাথে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাদীসের সাজুয্য লক্ষ্যণীয়। তিনি বলেছিলেন, তাঁর অনুসারীরা সবেমাত্র পৌত্তলিকতা ত্যাগ করে কা’বা নির্মাণ থেকে বিরত থেকেছেন।
রাসূলুল্লাহ (সা)-এর অনান্য আদেশ থেকেও এরূপ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়্। যেমন যদি অত্যাচারী-অনাচারী শাসককে হটিহটিয়ে সৎ ব্যাক্তির সরকার কায়েমের ক্ষমতা না থাকে তাহলে শাসকের অবিচার সহ্য করার কথা আছে। কেননা প্রতিবাদ করতে গিয়ে যেন বৃহ্ত্তর ফিতনার সৃষ্টি না হয়, মুসলমানদের অযথা রক্তপাত বা সামাজিক স্থিতিশীরতা যেন বিনষ্ট না হয় অথাৎ বাস্তব ফল ছাড়া কেবল অরাজকতা সৃষ্টি হতে পারে এমন প্রতিবাদের চেয়ে নীরবতাই কাম্য। অন্যথায় পরিস্থিতি এমনও হতে পারে যে, কুফরী অথবা রিদ্দাহর দিকেও মোড় নিতে পারে। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, “যতোক্ষণ না তুমি প্রকাশ্য কুফরী প্রত্যক্ষ কর যার পক্ষে তোমার কাছে আল্লাহ্র তরফ থেকে প্রমাণ আছে।” ((বুখারী, মুসলিম)
দু’টি দৃষ্টান্ত অনিশ্চিত সাফল্যের মুখে ঐক্য বজায় রাখার ওপর আলোকপাত করেছে। পক্ষান্তরে ইসলামী শিক্ষা পালনে ক্ষেত্রে যেসব ভাববাদী মুসলমান চরম পূর্ণতা দেখতে চায় অযথা যারা একেবারে বর্জন করতে চায় তাদের উভয়ের জন্যে এই ঘটনাগুলো শিক্ষণীয়। এদের কাছে কোনো মধ্যপন্থা নেই। ভাববাদীরা মুন্কার উচ্ছেদ শক্তি প্রয়োগকেই শেষ হাতিয়ার মনে করেন। তারা অন্য দু’টি পথ অর্থাৎ কথা ও হৃদয় দিয়ে প্রতিরোধের কথা বেমালুম ভুলে যান। মোটকথা, প্রতিটি উপায় প্রয়োগ নির্ভর করে ব্যাক্তির ক্ষমতা ও পরিস্থিতির ওপর। আশ-শরীয়াহ বিভিন্ন পরিস্থিতি ও প্রয়োজনের কথা বিবেচনা করার ওপর এতো দূর গুরুত্ব দিয়েছে যে, নিরূপায় অবস্থায় হারামও হালাল হয়ে যায় এবং ওয়াজিব স্থগিত হয়। ইমাম ইবনে তাইমিয়া (র) এবিষয়ে বুদ্ধিসীপ্ত আলোচনা করেছেন। তিনি লিখেছেন:
“আল্লাহ্ তা#য়ালা কুরআনুল করীমে বিভিন্ন জায়গায় বলেছেন যে, তিনি ক্ষমতার বাইয়ে অতিরিক্ত বোঝা মানুষের ওপর চাপাতে চান না।” তিনি বলেন, “আল্লাহ্ কারো ওপর এমন কোন কষ্টদায়ক দায়িত্ব অর্পণ করেন না যা তার সাধ্যাতীত।” (২:২৮৬) “আমরা কাউকেই তার সাধ্যাতীত অর্পণ করি না।” (৭:৪২)
“কাউকেই তার সাধ্যতীত কার্যভার দেয়া হয় না এবং আল্লাহ যাকে যে সামর্থ দিয়েছেন তদপেক্ষা গুরুতর বোঝা তিনি তার ওপর চাপন না।” (৬৪:১৬) ঈমানদারই তাঁর কাছে প্রার্থনা করেছে: “হে প্রভু, আমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর যেমন গুরুদায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন আমাদের ওপর তেমন দায়িত্ব অর্পণ করবেন না। হে প্রভু! এমন ভার আমাদের ওপর অর্পণ করবেন না যা বহন করার শক্তি ্আমাদের নেই।” (২:২৮৬)
আল্লাহ্ তাদের প্রার্থনা কবুল করেছেন। এসব আয়াত প্রমাণ করেছে যে, তিনি মানুষের ওপর এমন বোঝা চাপান না যা সে বহন করতে পারবে না। এটা নিশ্চিত যে, জাহমিয়া, কাদিরিয়া ও মুতাযিলা দর্শনের সাথে এর কোনো সংগতি নেই। এখানে একটি বিষয় পরিষ্কার বুঝে নিতে হবে যে, যদি কোনো শাসক, ইমাম, বুদ্ধিজীবি, ফকীহ অথবা মুফতী আল্লাহ্র খালেস ভয়ে তার সাধ্য অনুযায়ী যে ইজতিহাদ করবে তাহলে বুঝতে হবে আল্লাহ তার কাছ থেকে এটাই চেয়েছিলেন। তার সিদ্ধান্ত ভুল হোক, শুদ্ধ হোক, তাকে শাস্তি দেয়া হবে না। এর বিপরীত কাদিয়রা ও মুতাযিলারা যে ধারণা পোষণ করে তা বাতিল।
কাফিরদের বেলায়ও একই বিষয় প্রযোজ্য। যারা কুফরীর দেশে রাসূলের দাওয়াত পেয়ে তাঁকে রাসূল বলে স্বীকার করলেন এবং তাঁর ওপর অবতীর্ণ ওহীকে বিশ্বাস করে যথাসাধ্য আনুগত্য করলেন-যেমন নাজ্জাশী ও অন্যান্য, কিন্তু ইসলামের ভূখন্ডে যেতে না পরার দরুন শরীয়তকে সামগ্রিকভাবে মানতে পারলেন না; কারণ তাদেরকে দেশত্যাগের অনুতি দেয়া হয়নি অথবা প্রকাশ্যে আমলের সুযোগ পাননি এবং তাদেরকে সমগ্র শরীযাহ শিক্ষা দেয়ার মতো লোক ছিল না। এমন সকল মানুষের জন্যে আল্লাহ জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এরূপ আরো উদাহরণ আছে। আল্লাহ তায়ালা ফেরাউনের লোকদের মধ্যে যারা বিশ্বাসী ছিলো তাদের সম্পর্কে বলছেন: “এবং তোমাদের কাছে পূর্বে ইউসুফ এসেছিলেন স্পষ্ট নিদের্শন সহকারে, কিন্তু তিনি যা নিয়ে এসেছিলেন তাতে তোমরা বার বার সন্দেহ পোষন করতে। অবশেষে তিনি যখন ইন্তিকাল করলেন তখন তোমরা বলেছিলে, তারপরে আল্লাহ্ আর কাউকে রাসূল করে পাঠিবেন না।” (৪০-৩৪)
নাজ্জাশী খৃস্টানদের রাজা ছিলেন; কিন্তু তিনি তাদেরকে ইসলাম গ্রহণ করতে বললে তারা অস্বীকার করলো। কেবল মুষ্টিমেয় লোক তাকে অনুসরণ করেছিলো। তিনি যখন মারা গেলেন তখন তার জানাযা পড়ারও কেউ ছিলো না। রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনায় তার জানাযা পড়েন এবং উপস্থিত সকলকে বলেন, “আবিসিনিয়ায় তোমাদের মধ্যেকার একজন সৎ কমর্মশীল ভাই মারা গেছেন।” (বুখারী ও মুসলিম)
যদিও নাজ্জাশী ইসলামের অনেক শিক্ষা মানতে পারেননি, দেশত্যাগ করেননি, জিহাদে অংশ নেননি অথবা হজ্জ্ও করেননি। এটাও বর্ণিত আছে যে, তিনি পাঁচ ওয়াক্ত নামায, সিয়াম অথবা যাকাতের কতর্তব্য পালন করতে পারেননি; কেননা তার ঈমানের কথা প্রকাশ হয়ে পড়লে জনগণ তার বিরুদ্ধে চলে যেতে পারে। আমরা জানি, তিনি আল-কুরআনের বিধানও প্রয়োগকরেননি, যদিও আল্লাহ পাক তাঁর রাসূলকে আহলে কিতাবরা চাইলে তাঁর বিধান অনুযায়ী ফায়সালা করার আদেশ দিয়েছিলেন। আবার আল্লাহ্ তাঁর রাসূলকে এই মর্মে সতর্কও করে দিয়েছেন, “আহলে কিতাবরা যেন তাকে ওহীর অংশ বিশেষ খথেকেও বিচ্যুত করার জন্যে প্রলুব্ধ করতে না পারে।” কঠোর ন্যায়পরায়ণতার জন্যে উমর ইবনে আবদুল আজীজ (রা)-কে অনেক বিড়াম্বনা সইতে হয়েছে। এজন্যে তাকে বিষ প্রয়োগও করা হয়েছিলো বলে জানা যায়। কিন্তু নাজ্জাশী এবং তার মতো অন্যরা এখন জান্নাতে শান্তিতে আছেন যদিও তারা শরীয়তকে পূর্ণরূপে পালন ও প্রয়োগ করার সুযোগ পাননি, বরং তাই করেছেন যা তাদের কাছে প্রযোজ্য মনে হয়েছে। (মাজমুয়া আল ফাতওয়া)
৪. আল্লাহর সৃষ্টি রীতির জ্ঞান
ইসলাম যুক্তি ও অনুসন্ধিৎসার ধর্ম। এ কারণে পর্যায়ক্রম, সহিষ্ণুতা ও ক্রমিক পূণর্ণতার তাৎপর্য সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করা ইসলামের অন্যতম লক্ষ্য। মানূষ, বিশেষ করে তরুণদের মধ্যে দ্রুতির প্রবণতা অন্তর্নিহিত। অবশ্য এটি আমাদের যুগেরও বৈশষ্ট্য। এজন্যে আজ ফসল বুনে কালই তা কাটতে চায়। কিন্তু আল্লাহ্র সৃষ্টিরীতি অনুযায়ী এরূপ দ্রুতির কোনো অবকাশ নেই। গাছ থেকে ফল আহরণ করতে হলে এর পর্যায়ক্রমে অতিক্রম করতে দিতে হবে। মানুষের সৃষ্টি ত এর প্রকৃষ।ট নজীর। কুরআন বলছে:
“অতঃপর আমি শুক্রকে পরিণত করি রক্তপিণ্ড, তারপর রক্তপিণ্ডকে পরিণত করি মাংসপিণ্ডে, তারপর মাংসপিণ্ডকে পরিণত করি অস্থিপঞ্জরে, পরে অস্থিপঞ্জরকে মাংসে আবৃত করে দিই; অবশেষে তাকে গড়ে তুলি অন্য এক সৃষ্টিরূপে। অতএব সর্বোত্তম স্রষ্টা আল্লাহ্ কত মহান!” (২৩-১৪)
এমনিভাবে মানুষও শিশু থেকে পর্যায়ক্রমে প্রাপ্তবয়স্ক পরিণত হয়। একইভাবে আল্লাহ্র সুনান অনুযায়ী মানুষের জীবনেও বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে। অনুরূপভাবে আল্লাহ্র দ্বীন বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে অবশেষে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছে। তখন এই আয়াত নাযিল হয়েছে:
“আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পূর্ণাঙ্গ করলাম, তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম, এই ইসলামকেই তোমাদের দ্বীন মনোনীত করলাম।” (৫:৩) বিষয়টি অন্তত্য সহজ সরল; কিন্তু চারদিকের অবস্থা দেখে উৎসাহী তরুণরা এতোই বিক্ষুব্ধ যে, এই জ্ঞান তাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। তারা রাতারাতি ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করে সব সমস্যার সমাধানকরে ফোলতে চায়। তারা তাদের সম্মুখবর্তী বাধা-বিপত্তিকে লঘু দৃষ্টিতে দেখতে চায়। বস্তুত তাদের এই উভয় সংকটকে একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝানো যায়। এক ব্যক্তি আবু শিরিন (র) - কে একটি স্বপ্নের তাবির বলার অনুরোধ করেছিলো। সে স্বপ্ন দেখেছিলো যে, সে শুকনো জমিতে সাঁতার দিচ্ছে, ডানা ছাড়াই উড়ছে।” ইবনে শিরিন (র) তাকে বললেন, তিনিও এমন অনেক স্বপ্ন ও আকাংখা পোষণ করেন। হযরত আলী (রা) তার পুত্রকে হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলেন, “...ইচ্ছার ওপর নির্ভর করা থেকে সাবধান, এগুলো হচ্ছে আহাম্মকের উপকরণ।” অতএব এটা স্বতঃসিদ্ধ যে, বিপরীত বাস্তবতাকে কেবল ইচ্ছার হাতায়ার দিয়ে পাল্টানো যাবে না। প্রসঙ্গত একিট অমূল্য বইয়ের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি: ‘হাত্তা ইয়ুগাইয়িরু মা বিআনফুসিহিম’ (যতোক্ষণ না তারা নিজেরা পরিবর্তিত হয়)। এটি লিখেছেন সিরীয় মনীষী জাওদাত সাঈদ (র) বইটিতে আত্মা ও সমাজের পরিবর্তন ধারা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আলোচনার ভিত্তি হচ্ছে কুরআনের এই আয়াত : “নিশ্চয়ই আল্লাহ্ কোনো জাতার অবস্থা পরিবর্তন করেন না যতোক্ষণ না তারা নিজেদের অবস্থা নিজেরা পরিবর্তন করে।” (১৩ : ১১)
এবং ‘কারণ, আল্লাহ্ কোন সম্প্রদায়কে প্রদত্ত সৌভাগ্য পরিবর্তন করেন না যতোক্ষণ না তারা নিজেরাই পরিবর্তিত করে দেয় নিজের জন্য নির্ধারিত বিষয়।” (৮ : ৫৩)
বইটির ভূমিকার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ হচ্ছে : “মুসলিম তরুণদের মধ্যে অনেকেরই ইসলামের জন্য জান ও মাল কুরবানীর দৃঢ় প্রত্যয় রয়েছে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে এদের মধ্যে মাত্র মুষ্টিমেয় সংখ্যক তরুন জ্ঞানের একটি বিশেষ শাখায় অথবা দুর্বোধ্য সত্যকে উন্মোচিত করার লক্ষ্যে অধ্যয়নে উৎকর্ষ অর্জনে আগ্রহ প্রকাশ করে থাকে। উদাহরণস্বরূপ ঈমান ও আমল তথা বর্ণনা ও বাস্তবের শ্রণীবিভাগ ইত্যাদি সমস্যা রয়েছে। এসব বিষয় এমন সমস্যা সৃষ্টি করে যার বস্তুনিষ্ঠ ও তথ্যপূর্ণ সমাধান না হলে গঠনমূলক সংস্কার অসম্ভব। ইসলামী বিশ্ব এখনো গবেষণা ও লেখনীর র্মম উদ্ধার করেত পারছে না। কারণ তারা এখনো মনে করে যে, ‘মসির চেয় অসি শক্তিশালী।’ এজন্যেই আমাদের শিক্ষা-দীক্ষা স্তবিরতায় পর্যবসিত হয়েছে। ‘ঝাঁপ দেয়ার আগে চিন্তা করার কথা আমরা ভুলেই গেচি। ফলত উপরিউক্ত জ্ঞানের ক্ষেত্রে সর্বাত্মক বিভ্রান্তি বিরাজ করছে। এসবের মধ্যেকার পারস্পরিক সমন্বয় ও শৃংখলার বিষয়টি আমারা অধ্যায়ন বা উপলব্ধির চেষ্টা করছি না।
তদুপরি মুসলিম বিশ্বে ঈমানের অবস্থা সম্পর্কেও আমরা এখানে সতক”র্ পর্যালেচনা করছি না। এটার অর্থ এই নয় যে, মুসলমানদের ইমান ও ইসলাম সম্পর্কে মৌলিক জ্ঞান নেই। আমরা বরং মানসিক অবস্থার কথা বলতে চাই যা অবশ্যই মনের গহীন থেকে পরিবর্তন করতে হবে। আর ঐ পরিবর্তনই কেবল সৃষ্টিতে সক্ষম।
আত্মত্যাগ ও সাদকার প্রকৃত মর্ম গভীরভাবে উপলব্ধি না করে এখনো বিশ্বাস করা হয় যে, ঐ দু’টো সবচেয়ে মহত্তম পুণ্য। সুপরিকল্পিত ও সুচিন্তিত কৌশলের অনুপস্থতিতে কেবল কুরবানী করলেই এর লক্ষ্য অর্জিত হতে পারে না। অবুঝ বিশ্বাস তরুণ মনে জানমাল কুরবানীর আবেগ সৃষ্টি করে বটে, এর তাৎপর্য অধ্যয়ন ও উপলব্ধির চেতনা সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয়। তাৎক্ষণিক ভাবাবেগ বা চাপ থেকে কুরবানীর প্ররণা আসে; কিন্তু জ্ঞানের অন্বেষার জন্যে দাকার অবিশ্রান্ত অধ্যবসায়, চৈতন্য, অন্তদৃষ্টি ও সমীক্ষার মানসিকতা। আর এটিই পরিশেষে নিশ্চত সাফল্যের সম্ভাবনা সমুজ্জ্বল করে।
অবশ্য কোনো কোনো তরুণ বিভিন্ন বিভাগে অধঘ্যয়ন-পঠনের কাজে মনোনিবেশ করলেও শেষাবধি একঘেঁয়ে ক্লান্তি অনুভব করে উৎসাহ হারিয়ে ফেলে এবং জ্ঞান-গবেষণা হিমাগারে আশ্রয় নেয়। আমাদেরকে গভীর পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে এই জড়তা ও স্থাবিরতার কারণ খুঁজে বের করতে হবে।
আত্মোপলব্ধি ও আত্মসচেতনতা ছাড়াই দ্রুত পরিবর্তন সাধনের প্রবণতা অবান্তর। বিদ্যমান বাস্তবতার প্রতিক্রিয়া উলব্ধি এক জিনিস, আমাদের নিজস্ব ভূমিকা সম্পর্কে সচেতনতা অন্য জিনিস। এ ব্যাপারটি গুরুত্বপূর্ণ বিধায় আল কুরআনের এই শিক্ষার ওপরেও আলোকপাত করা হয়েছে। কুরআনে সমস্যার অন্তস্থল হিসেবে খুদী বা অহমকে চিহ্নিত করা হয়েছে, বাইরের অসদাচরণ বা অনাচার নয়। কুরআনুল করীমে সম্পদের যে কাঠামো নির্ধারণ করা হয়েছে তার মূল কথা হলো এটাই। এই সহজ সরল সত্যটি উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হলে আমাদের দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়ে যায় এবং এই তখন নৈরাশ্য, বৈরাগ্য ও স্বৈরাচারী দর্শনের উদ্ভব ঘটে।
অতএব মারাত্মক স্বআরোপিত অবিচার হচ্ছে মানুষ, মহাজগত ও সমাজের অন্ত র্নিহিত অনুষঙ্গ অনুধাবনে ব্যর্থতা। ফলত কোন্ অবস্থানে নিজেকে স্থাপিত করলে মানুষ আল্লাহ্র সুনান (রীতি) অনুযায়ী মানবীয় ও প্রাকৃতিক সম্ভাবনাকে সর্বোত্তম উপায়ে আহরণ করতে সক্ষম, তার বিচার করতে ভুল করে সে ব্যর্থতার গ্লানি বহন করে। এই দৃষ্টিতে, সমস্যার সম্মুখীন হলে দু’টি মানসিকতার উদ্ভব হয়। প্রথমত, এটা বিশ্বাস করা যে, সমস্যাটি নির্দিষ্ট ধারায় নিয়ন্ত্রিত করা সম্ভব। দ্বিতীয়ত, এই বিশ্বাস দ্বারা চালিত হওয়া যে, এটি রহস্যময় ও অতিপ্রাকৃতিক, অতএব কোনো রীতি দ্বারা ্এটি নিয়ন্ত্রণযোগ্য নয়। এই দুই চরম মানসিকতার মাঝে বহুবিধ মধ্যবর্তী দৃষ্টিভঙ্গিও রয়েছে যা মানুষের অনুসৃত পন্থা, আচার-আচরণ ও ফলাফল থেকে আঁচ করা যায়।
ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী মুসলমানদের জীবন নির্বাহে ব্যর্থতা একটি সমস্যা যা সহজেই অনুমেয়। এটি মেনে নিলেও প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে উপরিউক্ত দৃষ্টিভঙ্গির কোন্টি মুসলমানদের পোষণ করা উচিত? বস্তুত এরূপ আলাপ-আলোচনার মাধ্যমেই সচেতনতা সৃষ্টি করলেই মুসলমানরা সমস্যার সমাধানে কোন্ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করবে এবং কোন্টি পরিহার করবে তা নির্ণয়ে সহায়ক হবে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে, দুই দৃষ্টিভঙ্গি গুলিয়ে গিয়ে প্রতিটিই অবান্তর হয়ে গেছে। সুতরাং এর সমাধান বহুলাংশে নির্ভর করে পরিচ্ছন্ন অন্তর্দৃষ্টি উপর।”
সুনান ও সাফল্যের শর্তে
নিচে আমার ও একজন তরুণ মুসলমানদের মধ্যকার সংলাপ তুলে দিলাম। আমি কি তার প্রশ্নের জবাব দিই।
প্রশ্ন: আমরা কি সত্যের অনুসরণ করছি এবং আমাদের বিরোধীরা কি বাতিলের অনুসরণ করছে?
উত্তর: জী, হ্যা।
প্রশ্ন: আমাদের প্রভু কি ওয়াদা করেননি বাতিলের ওপর হক এবং কুফরির ওপর ঈমানের বিজয় হবে?
উত্তর: অবশ্যই, আল্লাহ কখনো তাঁর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না।
প্রশ্ন: তাহলে আমরা কিসের জন্যে অপেক্ষা করছি? আমরা বাতিলের বিরুদ্ধে কেন যুদ্ধ ঘোষণা করি না?
উত্তর: আমাদের ধর্ম শিক্ষা দেয় বিজয়ের জন্য শর্ত ও সুনান আছে। এটা আমাদের মানতে হবে। এই বিবেচনা না থাকলে রাসূলুল্লাহ (সা) মক্কী যুগে প্রথমেই পৌত্তলিকতার বারুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতেন। মূর্তি-অধ্যুষিত হওয়া সত্ত্বেও কা’বায় সালাত আদায় করা তাঁর পক্ষে অসহনীয় মনে হতো। প্রশ্ন: এই সুনান ও শর্ত কি?
উত্তর: প্রথমত, কেবল হক বলেই হক আল্লাহ্ বিজয়ী করেন না। তিনি সৎকর্মশীল লোকদের সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার ফলেই বিজয় দান করেন। কুরআনে পরিষ্কার বলা হয়েছে: “তিনিই তোমাকে স্বীয় সাহায্য ও মুমিনদের দ্বারা শক্তিশালী করেছেন। তিনি তাঁদের পরস্পরের হৃদয়ে প্রীতি স্থাপন করেছেন।” (৮:৬২-৬৩)
প্রশ্ন: কোথায় সেই ফেরেশতা যাঁরা হকের পক্ষে ও বাতিলের বিরুদ্ধে সাহায্যে করেছিলেন-যেমন তাঁরা বদর, খন্দক ও হুয়ানের যুদ্ধে সাহায্য করেছিলেন?
উত্তর: আল্লাহ যখন ইচ্ছে করবেন তখন ফেরেশতারা মুমিনদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসবেন। কিন্তু তাঁরা শূন্যের মধ্যে অবতীর্ণ হবেন না। দুনিয়ায় হকের জন্য সংগ্রামরত সত্যিকার প্রয়োজন হবে এবং যাদেরকে শক্তিশালী করার জন্যে আল্লাহ্র সাহায্যের প্রয়োজন হবে। বদরের যুদ্ধের সময় নাযিলকৃত আয়াত থেকে এটা পরিষ্কার বোঝা যায়: “স্মরণ করো, তোমাদের প্রভু ফেরেশতাদের প্রতি প্রত্যাদেশ করেন: আমি তোমাদের সাথে আছি। সুতরাং মুমিনদের অবিচলিত রাখ। যারা কুফরি করে আমি তাদের হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার করবো। (৮:১২)
প্রশ্ন: সত্যিকার ঈমানদার আছে কি? তাতেই কি বিজয় নিশ্চিত হবে?
উত্তর: তাদেরকে যথাসাধ্য ইসলামের প্রচার চালিয়ে তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করে এমন পর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে যাএ শত্রুর শক্তি সাথে ভারসাম্য সৃষ্টি হয়। একজনের পক্ষে একশ’ বা হাজারেরর বিরুদ্ধে লড়াই করা অযৌক্তিক হবে। কুরআনুল করীমে যে ভারসাম্যের কতা বলা হয়েছে তাতে একজন সত্যিকার মুমিন দশ জনের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে:
“হে নবি! ঈমানদারদেরকে যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করুন। তোমাদের মধ্যে যদি বিশ জন ধৈর্যশীল থাকে তারা দু’শ জনের ওপর জয়ী হবে এবং তোমাদের মধ্যে একশ’ জন থাকলে এক হাজার কাফিরের ওপর বিজয়ী হবে।” (৮:৬৬) প্রশ্ন: কিন্তু আমাদের প্রতিপক্ষ সদা সতর্ক, তারা অন্তর্ঘাতী কৌশলে উৎকর্ষতা লাভ করেছে।
উত্তর: এ থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, এমন একটি অপরিহার্যশর্ত আছে যা ছাড়া বিজয় সুনাশ্চিত হতে পারে না। তা হচ্ছে, বিপদ ও কষ্টে সহিষ্ণুতা ও উস্কানির মুখে দৃঢ়তা। রাসূলুল্লাহ (সা) আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-কে বলেন, “সহিষ্ণুতা বিজয়ের একটি পূর্ব শর্ত।”
আল্লাহ্ পাক স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা)-কে এই উপদেশ দিয়েছেন: “তোমার ওপর যে প্রত্যাদেশ পাঠিয়েছি তুমি তা অনুসরণ করো এবং তুমি ধৈর্য ধারণ করো যে পর্যন্ত না আল্লাহ্র বিধান আসে এবং আল্লঅহ্ই সর্বোত্তম বিধানকর্তা।” (১০:১০৯) অন্য আরকেটি আয়াতে বলা হয়েছে, “ধৈর্য ধারণ করো, তোমার ধৈর্য তো হবে আল্লাহ্রই সাহায্যঅ তাদের দরুন দুঃখ করো না এবং তাদের ষড়যন্ত্রে তুমি মনঃক্ষুণ্ন হয়ো না। আল্লাহ্ তাদেকই সাথে আছেন যারা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং যারা ক্ষমাশীল।” (১৬:১২৭-১২৮)
আল্লাহ্ আরো বলেন: “অতএব তুমি ধৈর্য ধারণ কর, নিশ্চই আল্লহ্র ওয়াদা সত্য। যারা দৃঢ় বিশ্বাসী নয় তারা যেন তোমাকে বিচলিত না করতে পারে।” (৩০-৬০) আল্লাহবলেন: “অতএব তুমি ধৈর্য ধারণ কর যেমন ধৈর্য ধারণ করেছিলেন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ রসূলগণ।” (৪৬-৩৫)
এবং আল্লাহ্ আরো বলেন: ধৈর্য ধারণ কর তোমার প্রভুর আদেশের অপেক্ষায়। তুমি আমার চোখের সামেনই আছ। তুমি তোমার প্রভুর সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর যখন তুমি শয্যা ত্যাগ কর। (৪৬:৩৫)
প্রশ্ন: কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সাফল্য ছাড়া আমরা দীর্ঘদিন কি ধৈর্য ধারণ করতে পারব?
উত্তর: কিন্তু আপনারা কি ইতিমধ্যে একটি অজ্ঞ লোককেও শিখ্ষা দেবেন না, কাউকে কি সৎপথে আনবেন না অথবা কাউকে কি তওবায় অনুপ্রাণিত করবেন না? যখন সে ইতাবচক জবাব দিলো তখন আমি বললাম, এটাই হচ্ছে আমাদের বিরাট সাফল্য যা আমাদেরকে আমাদের লক্ষ্যের কাছাকাছি নিয়ে যাচ্ছে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন: “আল্লহ্ যদি একটি লোককেও তোমার চেয়েও অনেক উত্তম।” তাছাড়া আমাদের কাছে দাওয়াত পৌছানোর ব্যাপারেই কৈফিয়ত চাওয়া হবে, আমরা নিজেরা তাতে সফল হলাম কিনা তা নয়। আমাদেরকে অবশ্যই ভালবাসার বীজ বপণ করতে হবে এবং আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করতে হবে যাতে উত্তম ফসল পাওয়া যায়। আল-কুরআন সবর্ত্রই আমাদের পথ-প্রদর্শক: “এবং বলো, তোমরা আমল করতে থাক। আল্লাহ্ তো তোমাদের কর্যকলাপ লক্ষ্য করবেন এবং তাঁর রাসূল ও মুমিনগণও করবে এবং তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতার নিকট, অতঃপর তিনি তোমরা যা করতে তা তোমাদেরকে জানিয়ে দেবেন।” (৯:১০৫)
চতুর্থ অধ্যায়
মুসলিম তরুণদের প্রতি উপদেশ
‘আলউম্মাহ’ ম্যাগাজিনে প্রকাশিত আমার প্রবন্ধে আমি মুসলিম তরুণ পুনর্জাাগরণের ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিক নিয়ে আলোচনা করেছি। তাতে আমি পরিশেষে দু’টি বিষয়ের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছি।
প্রথম: এই পুনর্জাগরণ একটি স্বাভাবিক ও সুস্থ চেতনার ইঙ্গিতবাহী। এর মাধ্যমে আমরা প্রকৃতি ও মূলের দিকে অর্থাৎ ইসলামের দিকে ফিরে যাচ্ছি। ইসরামই হচ্ছে আমাদের জীবনে প্রথম ও শেষ। এখানেই আমরা বিপদে আশ্রয় নিই, এখানে থেকেই আমরা শক্তি সঞ্চয় করি।
আমাদের সমাজ পূর্ব ও পশ্চিমের কাছ থেকে ধার মতবাদ দিয়ে সমস্যা মাধানের চেষ্টা করেছে। কিন্তু আধ্যাত্মিক ও বৈষয়িক উন্নতিসহ সকল ক্ষেত্রে উন্নয়নের এই চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। ফলে এখন আমাদের জনগণ ইসলামের অনিবার্য সমাধানে বিশ্বাস করে অথাৎ জীবনের সকল ক্ষেত্রে ইসলামী শারীয়াহর বাস্তবায়ন চায়। অতএব এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই যে, মুসলিম তরুণদের সাহস ও দৃঢ় সংকল্প নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে।
দ্বিতীয়: আমাদের কিছু কিছু তরুণের মধ্যে যে গোঁড়ামি রয়েছে তা হিংসা ও হুমকি দিয়ে পরিশুদ্ধ করা যাবে না। আল্লাহ্র দ্বীনের প্রতি এদের নিষ্ঠা ও আন্তরিকতায় আমাদের কোনো সন্দেহ থাকা উচিত নয়। একমাত্র প্রতিকার হচ্ছে সদিচ্ছা ও আন্তরনিকতা নিয়ে তাদের সাথে মেলামেশা করে তাদের মন-মানসিকতা উপলব্ধি করা এবং বুদ্ধিবৃত্তিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে ব্রান্ত ধারনা দূর করতে উদ্যোগী হওয়া।
আমি কেবল আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে মুসলিম তরুণদের এ ব্যাপারে অনেক উপদেশ দিয়েছি। রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন যে, ঈমানদারদের একে অপরের সাথে সর্বদা পরামর্শ করা উচিত এবং ধৈর্যের সাথে সৎকাজের আদেশ দেয়া এবং অসৎ ও অবাঞ্ছিত কাজ থেকে বিরত থাকা। ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনে পুরস্কার লাভের জন্যে এটি আবশ্যকীয় শর্ত। নিচে আমি আরো কিছু উপদেশ দিচ্ছি:
আমরা বিশেষজ্ঞ জ্ঞানের যুগে বাস করছি। জ্ঞানের একটি শাখায় ব্যুৎপত্তির মানে আরেকটি শাখায়ও পারদর্শী হওয়া নয়। যেমন একজন ইঞ্জিনিয়ারের সাথে চিকিৎসা বিষয়ে পরামর্শ করা যায় না অথবা একজন চিকিৎসকের সাথে আইনের পরামর্শ চাওয়া হাস্যকর। অতএব শারীয়ারহর জ্ঞানও সকলের সমান মনে করা ভুল। এটা ঠিক যে, ধর্মীয় জ্ঞানের শ্রেণী বিশেষের একচোটিয়া অধিকার ইসলাম স্বীকার করে না, যেমন খৃস্টানদের যাজক গোষ্ঠী রয়েছে বা হিন্দুদের ব্রাহ্মণবর্গ। কিন্তু ইসলাম ধর্মীয় জ্ঞানের জ্ঞানে বিশেষজ্ঞদের অস্তিত স্বীকার করে যারা কোনোভাবেই একটি বিশেষ গোষ্ঠী, শ্রেণী আ উত্তরাধিকারসূত্রে বংশগত নয়। বাস্তব কারণেই ধর্মীয় ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কুরআন বলেছে: “সকর মুমিনকে এক সাথে অভিযানে বের হওয়া উচিত নয়, তাদের প্রতিটি দলের এক অংশ বহির্গত হয় না কেন, যাতে তারা দ্বীন সম্বন্ধে জ্হান অনুশীলন করতে পারে এবং তাদের সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পারে, যখন তারা তাদের কাছে ফিরে আসবে, যাতে তারা সতর্ক হয়।” (৯:১২২)
কুরআন ও সুন্নাহর যেসব বিষয়ে আমাদের জ্হান নেই তা বিজ্ঞ ও অবিজ্ঞ লোকদের কাছ থেকে শিখতে বলেছে: “তোমার পূর্বে আমি ওহীসহ মানুষই পাঠিয়েছিলাম, তোমরা যদি না জান তবে জ্ঞানীদের জিজ্ঞাসা করো।” (২১:৭)
এবং “যখন শান্তি অথবা শঙ্কার কোন সংবাদ তাদের কাছে আসে তখন তারা তা প্রচার করে থাকে। যদি তারা তা রাসূল অথবা তাদের মধ্যে যারা ক্ষমতার অধিকারী তাদের গোচরে আনত, তবে তাদের মধ্যে যারা তথ্য অনুসন্ধান করে তারা তার যথার্থতা নির্ণয় করতে পারত।” (৪:৮৩)
আরেকটি আয়াতে আল্লাহ্ বলেন, “সর্বজ্ঞের ন্যায় তোমাকে কেউই অবহিত করতে পারে না।” (৩৫:১৪)
রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জানানো হলো যে, একজন আহত ব্যক্তিকে এই ফতোয়া দেয়া হয়েছে যে, অযু ও নামাযের আগে তার গোটা শরীর ধুয়ে ফেলতে হবে, যার ফলে তার মৃত্যু হয়েছে।তখন তিনি বললেন: “তারা তার মৃত্যু ঘটিয়েছে, আল্লাহ্ তাদেরও মৃত্যু ঘটান। সঠিক জানা না থাকলে তাদের কি জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল না?”এটা খুব বেদনাদায়ক যে, কোনো কোনো লোক অযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও জটিল বিষয়েও য়তোয়া দিতে অভ্যস্ত যা অতীত বর্তমান আলিমদের ফতোয়ার বিরোধী। তারা আগের আলিমদেরকে অজ্ঞ বলতেও কসুর করে না। তারা দাবী করে ইজতিহাদের দরজা সকলের জন্যে খোলা। এটা সত্য, কিন্তু ইজতিহাদের কতকগুলো শর্ত আছে যা এদের মধ্যে নেই। আমাদের পূর্ববর্তীরা তো অনেক বিজ্ঞ লোককেও সতর্ক বিবেচনা ছাড়া তাড়াতাড়ি ফতোয়া দেয়ার জন্যে সমালোচনা করেছেন। তারা বলেন, “কিছু কিছু লোক এত দ্রুত ফতোয়া দেয় অথচ তা হযরত উমার (রা)-এর কাছে পেশ করা হলে তিনি বদরের যুদ্ধের অংশগ্রহণকারী সকলের সাথে পরামর্শ করতেন এবং তারা আরো বলেন, “তোমাদের মধ্যে যারা ফতোয়া দেয়ার ব্যাপারে দুঃসাহসী (পাপ করে) দোযখে যাওয়ার ব্যাপারেও।” গভীর জ্ঞানের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তারা জটিল বিষয়ে বিজ্হ ব্যক্তিদের সাথে পরামর্শ করতেন। যেসব ফতোয়া মৌনভাবে দেয়া হতো ইসলামের প্রাথমিক যুগে সেগুলোকে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত বলে মেনে নেয়া হতো। কারো কাছে ফতোয়া চাওয়া হলে তারা পারত পক্ষে বিরত থাকতেন। আবার কেউ কেউ জানেন না বলে এড়িয়ে যেতেন।
উতবান ইবনে মুসলিম (রা) বলেন যে, একবার তিনি ৩০ মাস উমর (রা)-এর সং্গী ছিলেন। সে সময় উমর (রা)-কে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হয় এবং তিনি প্রায়শ বলতেন যে, তিনি জানেন না। ইবনে আবু লায়লা (রা) ১২০ জন সাহাবীর, (এঁদের মধ্যে অধিকাংশই আনসার), সম্পর্কে বলেছেন, “তাঁদের মধ্যে একজনকে জিজ্হেস করা হলে তিনি আরেকজনকে দেখিয়ে দিতেন, তিনিও আরেকজনকে দেখিয়ে দিতেন, তিনিও আরেকজনকে, এভাবে পালাক্রমে চলতো যতক্ষণ না প্রশ্নকর্তা আবার প্রথম ব্যক্তির কাছেই ফিরে যেতো।”
আতা ইবনে আস সাবির (র) বলেন যে, তিনি তার সমসাময়িক অনেককে ফতোয়া দিতে গিয়ে কাঁপতে দেখেছেন। তবিয়ুনদের মধ্যে সাঈদ ইবনে আল মুসাইয়েব (র) - কে কচিৎ ফতোয়া দিতে দেখা গেছে অথচ তিনি ফিকাহতে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন। যদি তিনি অনিচ্ছাকৃতভাবে ভুল করে থাকেন এবং তাদেরকেও রক্ষা করতে যদি তিনি অনিচ্ছাকৃতভাবে ভুল করে থাকেন এবং তাদেরকেও রক্ষা করতে যারা সেই ফতোয়া অনুসরণ করবে। মাযহাব চুষ্টয়ের ইমামগণও অনুরূপ সতর্কতা অবলম্বন করতেন। কোনো ব্যাপারে নিশ্চিত না হলে তারাও বলতেন যে, জানি না। ইমাম মালেক (র) বিশেষভাবে সতর্ক ছিলেন। তিনি বলেন, “কাউকে কোনে বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলে তার ‘জান্নাত ও জাহান্নম’ সম্পর্কে চিন্তা করা উচিত এবং জবাব দেয়ার আগে নিজের পারলৌকিক মুক্তি সর্ম্পকে ভাবা উচিত। ইবনে আল কাসিম (র) ইমাম মালিক (র) -কে বলতে শুনেছেন, “আমি একটা বিষয়ে দশ বছর ধরে গবেষণা করছি কিন্তু এখনো মনঃস্থির করতে পরিনি।” এবনে আবু হাসান (র) বলেন, “মালিককে ২১ টি বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, “তিনি মাত্র দু’টির ফতোয়া দিয়েছিলেন। তারপর বার বার বলেন, ‘আল্লাহ্ ছাড়া কোনো সাধ্য রবা ক্ষমতা নেই।” জ্ঞানের অম্বেষা থেকে তরুণদের নিরুৎসায়িত করা আমার উদ্দেশ্য নয়। দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত জ্ঞান অন্বেষণ করা আমাদের জন্যে ফরয। আমি যা বলতে চাই তা হচ্ছে তাদের জ্হান যতোই হোক, বিশেষজ্ঞদের সাহায্য নিতে তারা বাধ্য। আশ-শারীয়াহর জ্হানে বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা ও উসুল আছে যা জানা ও বোঝার সময় বা উপায় এই তরুণদের নেই।আমি বলতে চাই যারা কলেজে ভালো লেখাপড়া করে তাদেরকে সেটা ছেড়ে দিয়ে আশ-শারীয়ায় বিশেষজ্ঞ হতে হবে এমন প্রবণতা আমি অনুমোদন করি না। আরেকটি বিষয় বুঝতে হবে, এখন বিজ্হানে দক্ষতা অর্জনের জোর প্রতিযোগিতা চলছে। কোনো মুসলমান যদি আল্লাহ্র জন্যে বিজ্হানে বুৎপত্তি অজর্নের সাধনায় নিম্গ্ন হয় সে আসলেই ইবাদত ও জিহাদে অংশ নেয়।
এখানে স্মর্তব্য, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে ওহী নাযিল হওয়ার কালে তাঁর সাহাবীদের
বিভিন্ন পেশা ছিল। তিনি তাদেরকে নিজ নিজ পেশা ত্যাগ করে আসলাম অধ্যয়নের তাগিদ দেননি; অবশ্য তারা বাদে যাদেরকে এরূপ দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল কিংবা যাঁদের এ ব্যাপারে স্বাভাবিক ঝোঁক ছিল। আমার ভয় হয় অনেক হয়তো জনপ্রিয়তা বা নেতৃত্ব লাভের খায়েশ শরীয়ার জ্হানে দখল চাইতে পারে। মানুষকে প্রলুব্ধ করার জন্যে শয়তানের বহু রাস্তা আছে। অতএব আমাদের চিন্তা, উদ্দেশ্য ও কৌশল সম্পর্কে সতর্ক পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আত্মপ্রতারণার ফাঁদে পড়ে আমরা স্বচ্ছ চিন্তাকে যেন আচ্ছন্ন করে না ফেলি। আমাদেরকে সবর্দা কুরআনের এই আয়াত স্মরণ করা উচিত: “কেউ আল্লাহ্কে দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করলে সে পথে পরিচালিত হবে।”(৩:১০১)
যেহেতু জ্হানের প্রতিটি শাখা বিশেষজ্ঞদের দ্বারা পরিচিতি লাভ করে, অতএব তরুণদেরকে সৎ ও গভীর জ্হানের অধিকারী আলিম ও ফকীহদের কাঝ থেকে ধর্মীয় জ্হান হাসিলের উপদেশ দিচ্ছি। তাদের দেয়া ব্যাখ্যা ছাড়া সুন্নাহর ধর্মীয় জ্হানের প্রধান উৎস-জ্ঞানে সমৃদ্ধ হওয়া সম্ভব নয়। তাদেরকে অশ্রদ্ধা করা মূর্খতা ও ঔদ্ধত্য কুরআন-হাদীসে পারদর্শী হতে চান তাদের ইসলামী শিক্ষার ওপর নির্ভর করা যঅয় না। একইভাবে যারা উলামা ও ফুকাহার সিদ্ধান্তকে প্রধান অবলম্বন বানায়, কুরআন ও হাদীসকে উপেক্ষা করে, তাদের জ্হানের অবস্থাও হৃদয়বিদারক!
আবার অনেক আলিম আছেন যারা সরাসরি কুরআন হাদীসে অধ্যয়ন করেননি, কিন্তু ইসলামের ইতিহাস, দর্শন ও পূঁজিবাদ সম্পর্কে বিশেজ্ঞ। কিন্তু এরা অন্যকে শলিয়াহ শিক্ষা দেয়া অথবা ফতোয়া দেয়ার যোগ্য নন, কারণ তারা তাদের ভাষণে-বিবরণে প্রয়শ সত্যের সাথে পুরান, বিশুদ্ধকে শুদ্ধ, সারকে তারা নিজেরাও বোঝান না। এছাড়া যার আমল নেই তার শিক্ষা বা নেতৃত্ব দেয়ার অধিকার নেই। সততা, সাধুতা ও আল্লাহ্র ভীতি হচ্ছে প্রকৃত জ্ঞানের ফল। কুরআনুল কারীম বলছে, “আল্লাহ্র বান্দাদের মধ্যে যারা জ্ঞানী তারাই তাকে ভয় করে।” (৩৫:২৮)
এরূপ সাধুতা ও আল্লাহ্র ভয় একজন আলিমকে মূর্খতাসুলভ কাজ এবং শাসক অথবা সরকারের সেবাদাস হওয়া থেকে বিরত রাখে।
বিজ্হানের তৃতীয় বৈশিষ।ট্য হচ্চে ভারসাম্য। এটা ইসলামেরই অনুপম বৈশিষ্ট্য। দুর্ভাগ্যনকভাবে দু’টি প্রান্তিক প্রবণতা আমাদের রয়েছে: চরমপন্থা, শিরক, অবহেলা, গোঁড়ামি কিংবা বিচ্ছিন্নতা। আল-হাসান আল-বসরী (র) সাবধান করে দিয়ে বলেছেন, “চরমপন্থী উদাসীনদেন কার্যকলাপের দরুন দমৃ হারিয়ে যাবে।” প্রথম পক্ষ মাযহাব মানকবে কিন্তু ইজতিহাদের দরজা রুদ্ধ করে দেবে। দ্বীতিয় পক্ষ মাযহাব অস্বীকার করে তার সকল নীতি খন্ডনে প্রয়াসী হবে। এছাড়া আরেক দল কুরআন-হাদীসের আক্ষরিক অর্থ মেনে চলতে চায়। যা হোক দুই চরমের মাঝে আসল ইসলাম হারিয়ে যায়। অতএব আমাদের দরকান আরসাম্যময় সাধু ও সৎ চরিত্রের অধিকারী ফকীহ যারা সুচিন্তিতভাবে যুগের চাহিদাকে সামনে রেখে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে রায় দেবেন যা সাধারণ মানুষের জন্যে কল্যাণকর হবে। ইমাম সুফিয়ান আস-সাওরী বলেন, “সুস্পষ্ট যুক্তির ভিত্তিতে কোনো কিছুকে বৈধ করা জ্ঞানের পরিচায়ক, আর গোঁড়ামি তো যে কেউ নিষদ্ধ ঘোষণা করতে পারে।”
মুসলিম তরুণদেরকে গোঁড়ামি ও বাড়াবাড়ি পরিহার করতে হবে। একজন মুসলিম ঈমানে-আমলে সতর্ক হবে; কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, ধর্মীয় সহজ বিষয়গুলোকে উপেক্ষা করে ধর্মকে স্রেফ একটি কঠোর সতর্কবাণীতে পরিণতকরবে। কুরআন, সুন্নাহ, রাসূলুল্লাহ (সা) ও তাঁর সাহাবীরা বাড়াবাড়ির বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন; কেননা বাড়াবাড়ি আমলের বিষয়গুলোকে ঈমানদারদের জন্যে কষ্ঠকর করতে পারে। এ প্রসঙ্গে সিয়াম, পাকসাফ, বিবাহ ও কিয়াস সংক্রান্ত কুরআনের আয়াতগুলো লক্ষণীয়: “আর্লাহ্ তোমাদের জন্য যা সহজ তা চান এবং যা তোমাদের জন্য কঠিন তা চান না।” (২:১৮৫)
“আল্লাহ্ তোমাদেরকে কষ্ঠ দিতে চান না।” (৫:৬)
“আল্লাহ্ তোমাদের ভয়ের লঘু করতে চান, মানুষ সুষ্টগতভাবেই দুর্বল।” (৪:২৮) “হে ঈমানদারগণ! নিহতদের ব্যাপারে তোমাদের জন্য কিসাসের বিধান দেয়া হয়েছে। মুক্ত ব্যক্তির বদলে মুক্ত ব্যক্তি, ক্রীতদাসের পরিবর্তে ক্রীতদাস ও নারীর পরিবর্তে নারী। কিন্তু তার ভাইয়ের পক্ষ থেকে কীছুটা ক্ষমা করা হলে যথাযথ বিধির অনুসরণ করা ও সততার সাথে তার প্রাপ্য আদায় বিধেয়। এটা তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে ভার লাঘব ও অনুগ্রহ।”(২:১৭৮)
রাসূলের সুন্নায়ও নমনীয়তা ও ভারসাম্যের পক্ষে ও বাড়াবাড়ির বিরুদ্ধে হুঁশিয়ার করে দেয়া হয়েছে: “ধর্মে বাড়াবাড়ি থেকে সাবধান। তোমাদের পূর্বের (জনগোষ্ঠী) বাড়াবাড়ির জন্যে ধ্বংস হয়ে গেছে। ” (আহমদ, নাসাঈ,ইবনে মাজা) তারা ধ্বংস হয়েছ যারা চুল ছেঁড়াছেঁড়িতে লিপ্ত এবং রাসূলুল্লাহ (সা) এ হাদীসটি তিনবার উচ্চারণ করেন। (মুসলিম)
এছাড়া আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, “একবার এক বেদুঈন মসজিদে প্রস্রাব করেছিল। লোকজন তাকে মারতে গেল, কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা) তাদেরকে আদেশ দিলেন, “তাকে ছেড় দাও (প্রস্রাবের জায়গায়) এক বালতি অথবা এক গামলা পানি ঢেলে দাও। তোমাদেরকে সব কিছু সহজ করার জন্য পাঠানো হয়েছে, কঠিন করার জন্য নয়।” (বুখারী)
এটা সত্য যে, রাসুলূল্লাহ (সা) সব সময় দ’টির মধ্যে সহকটিকে বেছে নিতেন যদি তা পাপ না হয়। যকন জানতে পারেন যে, মুয়াজ (রা) নামায গীর্ঘায়িত করেন, তখন তিনি মুয়াজ (রা) -কে বলেন, “হে মুয়াজক! তুমি কি মানুষকে পরীক্ষা করছ?” (বখারী)
রাসূলুল্লাহ (সা) একথা তিনবার বললেন, “কেউ যদি কঠোরতার মাধ্যমে উৎকর্ষ অর্জনে আগ্রহী হয় তবে সে করতে পারে, কিন্তু অন্যকে বাধ্য করতে পারে না। এটা করতে গিয়ে সে অবচেতনভাবে অন্যকে ধর্ম থেকে সরিয়েও দিতে পারে।” রাসূলুল্লাহ (সা) - এর ওপরেই জোর দিয়েছেন। এজন্যে রাসূলুল্লাহ (সা) একাকী নামায দীর্ঘয়িত করতেন, কিন্তু ইমামাতির সময় সংক্ষিপ্ত করতেন। এ সংক্রান্ত একটি হাদীস ইতিপূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে।
মুসলিম (র) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইমামতির সময় কুরআনের চোট ছোট আয়াত পড়তেন। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) সহিষ্ণুতার নির্দশন হিসেবে একাদিক্রমে রোযা রাখার বিরুদ্ধে সতর্ক করে দিয়েছেন। কিন্তু লোকেরা তাঁকে বলল, “আপনি এরূপ করেন”। তিনি বলেন, “আমি তোমাদের মতো নই, আমার ঘুমের মধ্যে আমার প্রভু আমাকে কাদ্য ও পানীয় দান করেন।” ধর্মীয় বিষয়গুলো সহজরূপে তুলে ধরা এখন আগের চেয়েও বেশি প্রয়োজন। আমরা যে যুগে বাস করছি, সে যুগটি পাপপূর্ণ বস্তুবাদে নিমজ্জিত। এর মধ্যে ধর্মপালন দুঃসাধ্য বটে। এজন্যেই ফুকাহা কঠোরতার পরিবর্তে নমনীয়তার সুপারিশ করেছেন। দাওয়াতী কাজে কি পদ্ধতি আবলম্বন করা দরকার তা আগেই উল্লেখ করেছি। কুরআন বলছে: “তুমি মানুষকে তোমার প্রভুর পথে আহবান কর হিকমত ও সদুপদেশ দ্বারা এবং তাদের সাথে আলোচনা কর সদ্ভাবে।” (১৬:১২৫)
স্পষ্টত উক্ত আয়াতে শুধু মধুর কথা নয় সদয় অভিব্যক্তি কথাও বলা হয়েছে। এই লক্ষ্যে প্রথমে মতানৌক্যে নয়, মতৈনক্যের সূত্র ধরে আলোচনা শুরু করতে হবে। আলকুরআন বলছে: “তোমরা উত্তম পন্থা ব্যতীত আহলে কিতাবদের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয়োনা, তবে তাদের সাথে করতে পার, যারা তাদের মধ্যেসীমাংঘনকারী এবং বলো, আমাদের প্রতি ও তোমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে, তাতে আমরা বিশ্বাস করি এবং আমাদের ইলাহ ও তোমাদের ইলাহ তো একই এবং আমরা তাঁরই প্রতি আত্মসমর্পণকারী। (২৯:৪৬)
কোনো মতানৈক্যের বিষয় থেকে গেলে তা আল্লাহ্ স্বয়ং বিচার করবেন, “যদি তারা তোমার সাথে বিতণ্ডায় লিপ্ত হয় তবে বলো: “তোমরা যা কর সে ব্যাপারে আল্লাহ সম্যক অবহিত। তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করছ কিয়ামতের দিনে আল্লাহ্ পাক সে বিষয়ে তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করবেন।” (২২:৬৮-৬৯)
এই যদি অমুসলমানদের সাথে আচরণের পদ্ধতি হয় তাহলে মুসলমানদের সাথে মুসলমানদের কথাবার্তা কি রকম হওয়া উচিত। আমরা তো অনেক সময় আচার-আচরণে ‘আন্তরিক’ ও কর্কশে’র তফাতও ভুলে যাই। প্রকৃত দাইয়াকে মধুর ভাষণ ও সদয় অভিব্যক্তি দিয়ে দাওয়াতী কাজ চালাতে হবে। এমন প্রমাণ আছে যে, কর্কশ আচরণের ফলে আসল বিষয় বিকৃত বা বিলীন হয়ে গেছে। এগুলো থেকে আমাদের শিক্ষা নেয়া উচিত। এজন্যেই বলা হয়েছে: “যে ভঅল পথের আদেশ করে সে যেন তা ঠিক পথে করে।’
ইমাম গাজ্জালী(র) তাঁর ‘আমরু বিল মারুফ ওয়া নাহি আনিল মুনকার’ বইয়ে লিখেছেন, ‘যে ব্যক্তি ভাল কাজের আদেশ দেয় এবং নিষেধ করে খারাপ কাজ থেকে তার ধৈর্য, সহানুভূতি, জ্ঞান ও প্রজ্ঞা থাকতে হবে।‘ প্রসঙ্গত তিনি একটি ঘটনার উল্লেখ করেন। একবার এক ব্যক্তি খলীফা আল-মামুনের দরবারে এসে কর্কশ ভাষায় পাপ পূর্ণ্য বিষয়ক পরামর্শ দান শুরু করল। ফিকাহ সম্পর্কে আল-মামুনের ভাল জ্ঞান ছিল। তিনি লোকটিকে বললেন, “ভদ্রভাবে কথা বলো। স্মরণ করো আল্লাহ্ তোমার চেয়েও ভাল লোককে আমার চেয়েও একজন খারাপ শাসকের কাছে পাঠিয়েছিলেন এবং তাকে নম্রভাবে কথা বলার আদেশ দিয়েছিলেন। তিনি মূসা (আ) ও হারুন (আ)-কে যারা তোমার ভাল ফিরাউনের- যে আমার চেয়েও খারাপ ছিল-কাছে পাঠিয়েছিলেন এবং তাদেরকে আদেশ দিয়েছিলেন: ‘তোমরা দু’জন ফিরাউনের কাছে যাও, সে সকল সীমালংঘন করেছে, কিন্তু তার সাথে নম্রভাবে কথা বলো। হয়তোবা সে হুঁশিয়ারির প্রতি কর্ণপাত করবে অথবা (আল্লাহ্কে) ভয় করবে।” (২০:৪৩-৪৪)
এভাবে মামুন তর্কে জয়ী হলেন। আল্লাহ্ পাক মূসা (আ)-কে ভদ্র ভাষায় ফিরাউনের কাছ দাওয়াত পেশ করার শিক্ষা দিয়েছন।
মূসা (আ) ও ফিরাউনের মধ্যেকার সংলাপ পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ফিরাউনের ঔদ্ধত্য, নিষ্ঠুরতা ও লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সত্ত্বেও মূসা (আ) অত্যন্ত সতর্কতার সাথে দাওয়াত পেশ করৈছেন। সূরা আশশূরায় এ বিষয়টি লক্ষ্য করা যায়।
রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জীবন ও সুন্নহ অধ্যয়ন করলেও দেখা, মায়া, নম্রতা-সেখানে কর্কশতা ও কঠোরতার কোনো অবকাশ নেই। তাই কুরআন বলছে: “এখন তোমাদের মধ্য বেদনাদায়ক এবং তিনি তোমাদের ব্যাপারে খুবই উদ্বিগ্ন। তিনি ঈমানদারদের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু ও করুণাশীল।” (৯:১২৮)
সাহাবীদের সাথে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে কুরআন বলছে : “আল্লাহ্র দয়ায় তুমি তাদের প্রতি কোমল হৃদয় হয়েছে, তুমি যদি রূঢ় ও কঠোর হৃদয় হতে তাহলে তারা আশপাশ থেকে সরে যেতো।” (৩: ১৫৯)
একদিন একদল ইহুদী এসে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে সম্ভাষণ জানাল, “আস সামু আলাইকুম” যার আক্ষরিক অর্থ ‘আপনার মৃত্যু হোক’। হযরত আয়েশা (রা) ক্রুদ্ধ হয়ে জবাব দিলেন, “আলাইকুমুস সামু ওয়া আলানাহ” অথাৎ “তোমাদেরও মৃত্যু হোক, অভিশপ্ত হও তোমরা।” কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা) কেবর বললেন, ওয়া আলাইকুম (তোমাদের ওপরেও)” তারপর আয়েশা (রা)-কে লক্ষ্য করে বললেন, “যে সকল বিষয়ে দয়া করুণা করে আল্লাহ্ তাকে ভালবাসেন।” (সকল প্রামাণ্য সূত্রে সমর্থিত) তিনি আরো বললেন, দয়া সব কিছু সুন্দর করে। হিংসা সেগুলোকে ত্রুটিপূর্ণ করে।” (মুসলিম)
জুবায়ের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বর্ণনা করেন, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছেন: “যে কোমলতা থেকে বঞ্চিত সে সকল ভাল থেকে বঞ্চিত।” (মুসলিম) সকল ভাল থেকে বঞ্চিত হওয়ার চেয়ে বড় শাস্তি আর কী থাকতে পারে! আশা করা যায়, উপরের উদ্ধৃতিগুলো আমাদের বাড়াবাড়ি পরিহার করে প্রজ্ঞার পথে চালিত হওয়ার জন্যে যথেষ্ট। আমি আরো কয়েকটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই:
ক. মাতাপিতার প্রতি কর্তব্য অবশ্যই পালন করতে হবে। মাতাপিতা, ভাইবোন, কারো সাথেই এই অজুহাতে কর্কশ ব্যবহার করা যাবে না যে, তারা ধর্মের সীমালংঘনকরছে। তারা যদি এরূপ করেও তবুও তাদের সম্মান-স্নেহ পাওয়ার অধিকার ক্ষুণ্ণ হয় না। কুরআনে স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে: “তোমার পিতামাতা যদি তোমাকে পীড়াপীড়ি করে আমার সমকক্ষ দাঁড় করাতে যে বিষয়ে তোমাদর কোন জ্ঞান নেই, তুমি তাদের কথা মেন না। তবে পৃথিবীতে তাদের সাথে সদ্ভাবে বসবাস করবে এবং যে বিশুদ্ধ চিত্তে আমার অভিমুখী হয়েছে তার পথ অবলম্বন কর।” (৩১ “ ১৫)
অনুরূপভাবে পিতা ইবরাহীম (আ)-এর আচরণ থেকেও আমরা শিক্ষা নিতে পারি। কুরআনে এর বর্ণনা আছে। পিতাকে সত্য পথে আনার জন্য তিনি পিতার রূঢ়তা সত্ত্বেও তাকে কোমলতার সাথে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। তাহলে মুসলমান পিতামাতাদের সাথে কিরূপ আচরণ করতে হবে?
খ. সকল মানুষ এক, ইসলাম এই শিক্ষা দেয়। কিন্তু এ সম্পর্কে ভুল ধারণা থাকা উচিত নয়। মানুষে মানুলে অনেক ফার্থক্য আছে। তার মধ্যে বয়স একটি। এজন্যে শিষ্টতা ও সম্মানের দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশি, শাসকের অধিকারের দিকে খেয়াল রাখতে হবে। যবক সম্মান করবে বৃদ্ধকে, ইসলাম এই শিক্ষা দেয়। এ সম্পর্কে অনেক হাদীস আছে। যেমন: “বৃদ্ধ মুসলমানের প্রতি সম্মান আল্লাহ্র গৌরব।” (আবু দাউদ)
এবং “যে ব্যক্তি ছোটদের প্রতি স্নেহ, বৃদ্ধদের প্রতি সম্মান ও জ্ঞানীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না, সে আমার (উম্মতভুক্ত) নয়।” (আহমদ, তাবরানী, হাকিম)
গ. যারা দাওয়াতী কাজে অভিজ্ঞ, এক সময় খুব সক্রিয় ছিলেন, কোনো কারণে এখন ঝিমিয়ে পড়েছেন তাদের প্রতি সদয় দৃষ্টি রাখতে হবে। তাদের অবদানের কথা ভুলে গিয়ে তাদের নিন্দামুখের হওয়া উচিত নয়। এটাও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সুন্নাহ। হাতিব ইবনে আবু বালতাহ (রা) -এর ঘটনা থেকে এই শিক্ষা পাওয়া যায়। তিনি মক্কা বিজয়ের প্রস্তুতি সম্পর্কে খবর সরবরাহের বিনিময়ে মক্কায় অবস্থিত তাঁর পরিবার-পরিজনকে রক্ষার অনুরোধ করে পৌত্তলিক কুরায়েশদের কাছে বার্তা পাঠান। বার্তাটি ধরা পড়লে হাতিব স্বীকার করেন। তখন হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা) তার বিশ্বাসঘাতকতায় এতোই ক্রুদ্ধ হয়ে পড়েন যে, তিনি তার শিরচ্ছেদ করার জন্যে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে অনুরোধ করেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা) তা নাকচ করে দিয়ে বলেন, “তুমি কিভাবে জানো, আল্লাহ্ সম্ভবত বদরের যুদ্ধে অংশগহণকারীদের ভাল কাজ দেখেছেন এবং তাদেরকে বলেছেন: “তোমরা যা খুশী তাই করো। কেননা আমি মাফ করে দিয়েছি তোমাদেরকে (তোমাদের অতীত-ভবিষ্যতের পাপকে)।” প্রাথমিক যুগে হাতিবের ইসলাম গ্রহণ, বদরের যুদ্ধে তার শৌর্যবীর্যের কথা স্মরণ করে রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে ক্ষমা মঞ্জুর করলেন। এভাবে তিনি বদরের যোদ্ধাদের বিশেষ মর্যদা সম্পর্কেও সচেতন করে দিলেন।
ঘ. আমি মুসলিম তরুণদেরকে দিবাস্বপ্ন ও অবাস্তব ভাববাদিতা পরিহার করার উপদেশ দিচ্ছি। তাদেরকে ধূলোর ধরণীতে নেমে বড় বড় শহরের বস্তি ও গ্রামের নিপীড়ত মানুষের সাথে মিশতে হবে। এখানেই নির্ভেজাল পুণ্য, সরলতা ও পবিত্রতার উৎস নিহিত আছে। এসব মানুষ অভাবের তীক্ষ্ণ খোঁচায় দিশেহারা হয় না। এখানে সমাজ পরিবর্তন, পুনর্গঠন ও আন্দোলনের বিপুল উপাদান ছড়িয়ে আছে। এদের সাথে মেলামেশা করে তাদের অশিক্ষা-কুশিক্ষা দূর করে এবং তাদের খারাপ দিকগুলো বর্জন ও সুকৃতির বিকাশে উদ্যেগী হতে হবে। এজন্যে সংঘবদ্ধ ও সম্মিলিত প্রয়াস চাই। নিপীড়িতদের দুঃখ-কষ্ট লাঘব করা এবং তাদেরকে সঠিক পথে এনে জিহাদের কাতারে শামিল করার প্রচেষ্টাও ইবাদাহর মধ্যে গন্য। ইসলামে দাতব্য কাজে উৎসাহ দেয়া হয়, এটি ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত।
আবু হুরায়রাহ (রা) একটি হাদীসে বলেন: “মানুষের প্রতিটি সন্ধির জন্যে সাদাকাহ তার কাছ থেএক প্রাপ্য, প্রতিদিন যখন সূর্য ওঠে। দুই ব্যক্তির মধ্যে মীমাংসা করে দেয়াও সাদাকাহ, পশুর পিঠে চড়তে কাউকে সাহায্য করা অথবা মাল তুলে দেয়াও সাদাকহর অন্তর্ভুক্ত এবং একটি মধুর বচনও সাদাকাহ এবং কল্যণের দিকে প্রতিটি পদক্ষেপ একটি সাদাকাহ, পথ থেকে ক্ষতিকর জিনিস সরানোও সাদাকহ।” (সকল প্রামান্য সূত্রে সমর্থিত)
ইবনে আব্বাস (রা) আরেকটি হাদীসে বলেন, “প্রতিদিন একিট মানুষের প্রতিটি সন্ধির জন্যে তার কাছ থেকে প্রাপ্য।” শ্রোতাদের একজন বলল, “এটা আমাদের জন্যে কুবই কঠিন।” রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, তোমাদের বাল কাজের আদেশ, কারাপ ও অবাঞ্ছিত কাজ থেকে বারণ একটি সালাহ, দরিদ্রের জন্যে সাহায্য একটি সালাহ, রাস্তা থেকে ময়লা সরানোরও একটি সালাহ ও সালাহর পথে তোমার প্রতিটি পদক্ষেপ একটি সালাহ।” (ইবনে খুজায়মা)
বুরায়দা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, “মানুষের ৩৬০ টি অস্থি-সন্ধি আছে। তাকে অবশ্যই প্রতিটির জন্যে সাদাকাহ দিতে হবে।” তারা (সাহাবীরা) বললেন, “হে নবী, এটা কার পক্ষে সম্ভব?” তারা মনে করেছিলেন যে, এটা অর্থনৈতিক সাদাকাহ। রাসূলুল্লাহ (সা) তখন বললেন, “মসজিদে শ্ফেম্মার ওপরে কেউ যদি মাটি চাপা দেয় তাও সাদাকাহ, পথ থেকে বাধা সরানোও সাদাকাহ।” (আহমদ, আবু দাউদ, ইবনে খুজায়মা, ইবনে হাব্বান)
এ রকম তথ্য আরো বহু হাদীসে আছে। অন্ধ, বোবা, দুর্বলের ও দুস্থের প্রতি দয়া প্রদর্শনের উপদেশ রয়েছে এবং এসব কাজকে সাদাকাহ ও ইবদাহ বলে গণ্য করা হয়েছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে মুসলমান সর্বদা পুণ্য কাজের উৎস হিসেবে বিরাজমান। এভাবে অন্যেরও উপকার করছে, নিচের মধ্যেও সদগুণের বিকাশ ঘটাচ্ছে, সেই সাথে অসৎবৃত্তি অনুপ্রবেশের আশঙ্কা থেকে নিরাপদ থাকছে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, “সেই ব্যক্তি রহমতপ্রাপ্ত যাকে আল্লাহ্ সৎকর্মের চাবি এবং অসৎকর্মের তালা বানিয়েছেন।” (ইবনে মাজা)
অবশ্য অনেক ভাববাদী মনে করতে পারেন এতে দাওয়াতী কাজ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আমি মনে করি সামাজিক সম্পর্কটাই একটা বাস্তব দাওয়াহ। এই দাওয়াহ মানুষ আপন পরিবেশে পেয়ে থাকে। ইসলাম কেবল বুলি নয়। দাওয়াহ অর্থ মানুষের সমস্যার সাথে একাত্ম হওয়া, এর প্রতিকারের ব্যবস্থা করা। ইমাম হাসান আল বান্নাহ (র) এ ব্যাপারে সচেতন ছিলেন বলে ইসলামী আন্দোলনের সমাজ সেবা বিভাগ খুলেছিলেন সর্বত্র। তিনি মনে করতেন মুসলমানকে যেমন সালাতের শাধ্যমে ইবদতের তগিদ দেয়া হয়েছে তেমনি তাগিদ রয়েছে দাতব্য কাজেরও। কুরআনুল কারীমে বলা হয়েছে: “হে বিশ্ববাসিগণ, তোমরা রুকু কর, সিজদা কর এবং তোমাদের প্রতিপালকের ইবাদত কর ও সৎকাজ কর যাতে সফলকাম হতে পার এবং জিহাদ কর আল্লাহ্র পথে যেভাবে করা উচিত। তিনি তোমাদেরকে মনোনীত করেছেন। তিনি দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের ওপর কোন কঠোরতা আরোপ করেননি।” (২২ : ৭৭-৭৮)
উপরিউক্ত আয়াত মুসলিম জীবনের ত্রিমুখী ভূমিকার সংজ্ঞা দিয়েছে। আল্লাহ্র সাথে সম্পর্ক হচ্ছে ইবাদতের মাধ্যমে তার সেবা; সামাজিক ভূমিকা হচ্ছে দাতব্য কাজের মাধ্যমে সমাজের সেবা; বাতিল শক্তির সাথে সম্পর্ক হচ্ছে তার বিরুদ্ধে জিহাদ চালানো। এরপরেও হয়তো ভাববাধীরা আগে ভাগে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্টার কথাই বলবে এই যুক্তিতে যে, এটা হয়ে গেলে তো সব সমস্যারই সমাধান অটোমেটিক হয়ে যাচ্ছে। এতে কোনো সন্দেহ নেই ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা তো সমগ্র উম্মাহর দায়িত্ব। এজন্যে তো সময় ও অধ্যবসায় প্রয়োজন। এই প্রিয়তম উদ্দেশ্য অর্জনের পূর্ব পর্যন্ত তো আমাদেরকে সমাজের সেবা ও উন্নতির চেষ্টাও করতে হবে। এই তৎপরতা একাদারে ভবিষ্যত বংশধরদের গঠন, প্রস্তুতি ও উম্মাকে নেতৃত্ব দেয়ার ক্ষমতারও পরীক্ষা। এটা হচ্ছে এই রকম যে, একজনের এক্ষুণি চিকিৎসা দরকার, কিন্তু একজন ইসলামী ডাক্তার ইসলামী রাষ্ট্রের ইসলামী হাসপাতাল ছাড়া রোগীর চিকিৎসা করতে নারাজ। অতএব ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম না হওয়া পর্যন্ত সমাজ বা মানবতার সেবা কিংবা কোনো বিতর্কিত বিষয়ের মীমাংসা স্থাগিত রাখার যুক্তি হাস্যকর।
কাঙ্খিত ইসলামী রাষ্ট্রর রূপ সম্পর্কে আমার ধারণা: একটি জলপাই ও খেজুর গাছের বাগান ফল উৎপাদনমুখী কাজের চেষ্টা না করে জলপাই ও খেজুর ফলনের আশায় বসে থাকবে, এটা কি যুক্তিসঙ্গত? তাকে জীবিকার্জনের জন্যে অন্য কাজও করতে হবে, সেই সাথে কাঙ্খিত ফলের জন্যে জলপাই ও খেজুর গাছেরও যত্ন নিতে হবে।
ঙ. তরুণদের প্রতি আমার সর্বশেষ পিতৃস্নেহসুলভ উপদেশ হচ্ছে: হতাশার শৃংখল থেকে নিজেদের মুক্ত করুন এবং মুসলমানদের মধ্যে নির্মল ও সচ্চরিতের নমুনা হোন। অবশ্য এই আশাবাদের জন্যে আরো কয়েকটি বষয়ে সচেতন র্দৃষ্টি দিতে হবে: প্রথম : মানুষ ফেরেশতা নয়। পিতা আদম (আ) -এর মতো তারাও ভুল করতে পারে। আল-কুরআন আমাদের শিক্ষা দিয়েছে, “আমি তো আগেই আদমের প্রতি নির্দেশ দিয়েছিলাম, কিন্তু তিনি ভুলে গিয়েছিলেন, আমি তাকে সংকল্পে দৃঢ় পাইনি।” (২০ : ১১৫)
মানুষের ভ্রান্তি প্রবণতা ও প্রবৃত্তির প্রতি প্রলোভন স্বীকার করে নিলে আমরা অন্যের ভুলত্রুটির প্রতি সহনীয় ও সহৃদয় মনোভাব পোষণের পাশাপাশি তাদেরকে আল্লাহ্র ক্ষমারও আশা করতে পারব। আল্লাহ্ তায়ালা রাসূলুল্লাহ (সা) - কে উদ্দেশ্য করে বলছেন: “বল, হে আমার বান্দাগণ! তোমরা যারা নিজেদের ওপর যুলুম করেছ, আল্লাহ্র রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না, আল্লাহ্ সকল গুনাহ মাফ করে দেবেন। তিনি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।” (৩৯ : ৫৩)
উক্ত আয়াতে ‘আমার’ বান্দা বলার মাধ্যমে বান্দাদের জন্যে আল্লাহ্র উদ্বেগ ও দয়ার চিত্রই ফুটে উঠেছে।
দ্বিতীয় : এটা বোঝা আবশ্যক যে, মানুষের মনের গহীনে কী আছে তা আল্লাহ্ ছাড়া কেউ আর জানেন না। অতএব তার বক্তব্যের আলোকে তাকে বিচার করতে হবে। তাই কেউ যদি কালিমা পাঠ করে তাহলে তাকে মুসলমান হিসেবেই গণ্য করা উচিত। এটাও রাসূলুল্লাহ (সা) এর সুন্নাহ। তিনি বলেন “আমি আদেশ প্রাপ্ত হয়েছি (আল্লাহ্র দ্বারা ) সেই সব লোকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার যতোক্ষণ না তারা স্বীকার করবে যে, আল্লাহ্ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই এবং মুহাম্মাদ (সা) আল্লাহ্র রাসূল এবং সুচারুরূপে নামায পড়াবে, যাকাত দেবে। তারা সকলে যদি এরুপ করে তারা আমার কাচ থেকে (ইসলামী আইন প্রদত্ত শাস্তির বিধান ব্যতীত) জীবন ও সমাজ রক্ষাকরে এবং আল্লাহ্ তাদের হিসাব নেবেন।”
এ কারণেই তিনি মুনাফিকুনকে শাস্তি দেননি অথচ তিনি নিশ্চত ছিলেন যে, তারা তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত করছে। তাদেরকে হত্যা করার পরামর্শ এলে তিনি বলেন: “আমি ভয় করি লোকে বলবে যে, মুহাম্মদ (সা) তাঁর সাহাবীদের হত্যা করে।”
তৃতীয়: আমাদেরকে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের ওপর বিশ্বাস করে, সে যতো খারাপ করুক একেবারেই জন্মগতভাবে ভালোশূন্য হতে পারে না। বড় ধরনের পাপ করলে সে একেবারে ঈমানশূন্য হয়ে যায় না যতোক্ষণ না সে ইচ্ছাকৃত আল্লাহ্ কে অস্বীকার করে ও তাঁর আদেশ অবজ্ঞা করে। রাসূলুল্লাহ (সা) পাপাচারীকে চিকিৎসার দৃষ্টিতে দেখতেন যমন রোগীকে দেখা হয়। পুলিশের মতো তিনি অপরাধীকে দেখতেন না। ইনশাআল্লাহ নিচের ঘটনা থেকে বিষয়টি পরিস্কার হয়ে যাবে :
একজন কোরায়শী যুবক একদিন রাসূল্লাহ (সা)- এর কাছে এসে ব্যভিচারের অনুমতি চাইল। সাহাবীরা ক্রদ্ধ হয়ে তাকে শাস্তি দিতে উদ্যত হলেন; কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা) -এর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। শান্ত সমাহিত চিত্তে তিনি যুবকটিকে তার আরো কাছে আসতে বললেন। তারপর বললেন, “তুমি কি তোমার মায়ের জন্যে এটা (ব্যভিচার) মেনে নেবে?” যুবকটি জবাব দিল, “না।” রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, “(অন্য) লোকেরাও এটা তাদের জন্যে অনুমোদন করবে না।” অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) বারবার তাকে জিজ্ঞেস করলেন সে তার কন্যা, বোন ও চাচীর জন্যে অনুমোদন করবে কিনা? প্রতিবারই যুবক বলল, “না।” এবং প্রতিবারই রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, “(অন্য) লোকেরাও এটা তাদের জন্য অনুমোদন করবে না।” তারপর তিনি যুবকটির হাত ধরে বললেন, “আল্লাহ্ তার (তরুণের পাপ মার্জনা করুন, তার অন্তর পবিত্র করুন এবং তাকে সহিষ্ণু করুন (তার এই কামনার বিরুদ্ধে)।” (আহমদ, তাবরানী) এই সহৃদয় অনুবুতি সুস্পষ্ট সদিচ্ছা ও মানুষের জন্মগত সুমতির প্রতি আস্থার পরিচায়ক যা মানুষের খারাপ বৃত্তিগুলোকে বিদূরিত করতে সক্ষম। আর খারাপ প্রবৃত্তি ক্ষনস্থায়ী। সুতরাং তিনি ধৈর্যের ও যুক্তির সাতে তার সাথে আলাপ করে তার ভুল চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন। চরমপন্থীরা যুক্তি দেখাতে পারে যে, যুবকটি যেহেতু ব্যভিচার করেনি তাই তার প্রতি উদারতা দেখানো হয়েছে। তাহলে আরো একটি উদাহরণ দেখা যাক : এক মহিলা ব্যভিচারিণী গর্ববতী হয়ে রাসূলূল্লাহর (সা) - এর কাছে এসে দোষ স্বীকার করে তাকে পাথর ছুঁড়ে মেরে ফেলে পাপমুক্ত করার জন্যে বারবার চাপ দিতে লাগলো। তাকে পাথর মারার সময় খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রা) তাকে অবভিশাপ দিচ্ছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে বললেন, “খালিদ নম্র হও। যাঁর হাতে আমার জীবন তাঁর শপথ, সে এমন অনুশোচনা করেছে যে, এমনকি একজন দোষী খাজনা আদায়কারীও যদি অনুতপ্ত হতো তবে তাকেও ক্ষমা করা হতো।” (মুসলিম ও অন্যান্য)
কেউ কেউ যুক্তি দেখাবেন মহিলাটি পাপ করেই অনুতাপ করেছে। তাহলে আরো একটি উদাহরণ দিচ্ছি: রাসূলুল্লাহ (সা)- এর জীবদ্দশায় একজন মদ্যপায়ীকে বার বার রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে আনা হলো এবং বার বার তাকে শাস্তি দেয়া হলো, কিন্তু সে নেশা করতেই তাকলো। একদিন যখন তাকে একই অভিযোগে আবার হাযির করে তাকে বেত্রাঘাত করা হলো তখন এক ব্যক্তি বললো, “আল্লাহ তাকে অবিশপ্ত করুন! কতোবার তাকে শাস্তি দেয়ার জন্যে আনা হলো?” রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, “তাকে অভিশাপ দিও না, আল্লাহ্র শপথ, আমি জানি সে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুলকে ভালবাসে। রাসূলুল্লাহ (সা) আরো বলেন, “তোমার ভাইয়ের বিরুদ্ধে শয়তানকে সাহায্য কোর না।” রাসূরুল্লাহ (সা) তাদেরকে অবিশাপ দেয়া থেকে বারণ করলেন এ কারণে যে, এতে ঐ মানুষটি এবং তার মুসলিম ভাইয়ের মধ্যে মনোমালিন্য ও রেষারেষি সৃষ্টি করতে পারে কারণ-তার পাপ তাকে মুসলিম ভ্রাতৃত্বের বন্ধন থেকে বিচ্ছিন্ন করেনি। উপরিউক্ত ঘটনাবলী গভীরভাবে চিন্তা করলে আমরা বুঝতে পারব যে, মানুষের অন্তর্নিহিত সুকৃতির প্রতি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কী গভীর অন্তর্দৃষ্টি ছিল। অতএব যেসব চরমপন্থীরা কেউ ভুল করলেই তাকে নির্বিচারে কুফর-শিরকের ফতোয়া দেয়, তা তাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞতাপ্রসূত। একজন জ্ঞানী ব্যক্তি একদা বলেছিলেন : “অন্ধকারকে অভিশাপ দেয়ার পরিবর্তে রাস্তায় একটি মোমবাতি জ্বালানোর চেষ্টা করো।”
এই হচ্ছে আমার প্রিয় তরুণ মুসলমানদের প্রতি উপদেশ। আমার উদ্দেশ্য কুরআনুল কারীমে বর্ণিত হযরত শুয়াইব (আ) -এর ভায়ায় : ‘আমি আমার সাধ্য মতো সংস্কার করতে চাই। আল্লাহর মদদেই কিন্তু কাজসম্পন্ন হয়; আমি তাঁরই উপর নির্ভর করি এবং আমি তাঁরই অভিমুখী। (১১ : ৮৮)
পরিভষা সঙ্কেত
১. কিসা : সমতার আইন।
২. আস-সাহীহ : ছয়টি সহীহ হাদীস সংকলনের যে কোন একটি।
-- সমাপ্ত --
', 'ইসলামী পুনর্জাগরনঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা', '', 'publish', 'closed', 'closed', '', '%e0%a6%87%e0%a6%b8%e0%a6%b2%e0%a6%be%e0%a6%ae%e0%a7%80-%e0%a6%aa%e0%a7%81%e0%a6%a8%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%9c%e0%a6%be%e0%a6%97%e0%a6%b0%e0%a6%a8%e0%a6%83-%e0%a6%b8%e0%a6%ae%e0%a6%b8%e0%a7%8d-2', '', '', '2019-10-31 16:55:19', '2019-10-31 10:55:19', '
ইসলামী পুনর্জাগরনঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা
ইউসুফ আল কারযাভী
স্ক্যান কপি ডাউনলোড
লেখকের কৈফিয়ত
১৪০১ হিজরীর রমজান ও শাওয়াল মাসে (১৯৮১ খৃঃ) মুসলিম তরুণদের পুনর্জাগরণ সম্পর্কিত আমার দু’টি প্রবন্ধ ‘আল-উম্মাহ’ ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়। আমি এই জাগরণের ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় দিকের ওপর আলোকপাত করি। এটি এখন ব্যাপকভাবে মুসলিম পর্যবেক্ষক, ধর্মপ্রচারক, সুধীজনের বিবেচ্য বিষয়। আমি ঐ প্রবন্ধে মুসলিম তরুণদের পুনর্জাগরণের জোয়ারকে সঠিক খাতে প্রবাহিত করার লক্ষ্যে তাদের সাথে পিতৃসুলভ মনোভাব নিয়ে আলাপ-আলোচনা পরামর্শ দিয়েছিলাম। আমার মতামত মুসলিম বিশ্বে এমন ব্যাপক সাড়া জাগাতে সক্ষম হয় যে, আমার লেখাগুলো কয়েকটি ভাষায় অনুদিত হয়। অনেক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা আমার প্রবন্ধগুলো গুরুত্বের সাথে পাঠ করে, যদিও এতে আমি তাদের অনেকেরই সমালোচনা করেছি।
আমি আনন্দের সাথে এখানে উল্লেখ করছি যে, কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ইসলামী সংস্থা ১৯৮১ সালে তাদের গ্রীষ্মকালীন শিবিরে আমার মতামতগুলো নিয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা করে। তারা ঐ লেখাগুলো ছাপিয়ে প্রকাশ করে এবং আগ্রহী ব্যক্তিদের মধ্যে বিতরণ করে। এতে তাদের প্রশংসনীয় সচেতনার পরিচয় পাওয়া যায়; সেই সাথে মধ্যপন্থার প্রতি তাদের সমর্থনসূচক মনোভাবের প্রতিফলন স্পষ্ট হয়ে ওঠে।
আমি এখানে সাম্প্রতিক মুসলিম তরুণ ও ক্ষমাতাসীনদের মধ্যে সংঘাত সৃষ্টিকারী ঘটনা প্রবাহের ওপর আলোচনায় লিপ্ত হতে চাই না। এই আশঙ্কায় নয় যে, আমার আলোচনা উত্তেজনা প্রসারের কারণ হবে, বরং ‘আল-উম্মাহ’ ম্যাগাজিনের অবস্থানগত দিক বিবেচনা করেই আমাকে এই নীতি অবলম্বন করতে হয়েছে। কারণ, এই পত্রিকাটি বিশেষ একটি গ্রুপের নয়, বরং সমগ্র উম্মাহর স্বার্থ সমুন্নত করার মহান দায়িত্বে নিয়োজিত। আমি এখানে মূলত ধর্মীয় চরমপন্থা বা গোঁড়ামীর বিষয় নিয়ে আলোচনার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছি। কারণ এ থেকে উদ্ভুত ঘটনাবলী দীর্ঘ ও উত্তপ্ত আলোচনার কেন্দ্র বিন্দুতে পরিণত হয়েছে। আর এহেন বাক-বিতন্ডায় স্রেফ জ্ঞানী-গুনীরাই জড়িয়ে পড়ছেন না, ইসলাম সম্পর্কে এমন অজ্ঞ ব্যক্তিরাও এতে সোৎসাহে শামিল হচ্ছেন ইসলামের প্রতি যাদের শত্রুতা, অবহেলা ও বিদ্রুপ সুবিদিত। কয়েক বছর আগে আল-আরাবী পত্রিকার পক্ষ থেকেও “ধর্মীয় চরমপন্থা” স্বরুপ ও বৈশিষ্ট্য উদ্ঘাটন করে আমাকে লেখার অনুরোধ জানানো হয়েছিল। ১৯৮২ সালের জানুয়ারী মাসে প্রবন্ধটি প্রকাশিত হলে আমার কতিপয় বন্ধু আমাকে এই বলে দোষারোপ করলেন যে, আমি নাকি এমন এক বিষয়ে কলম ধরেছি যেখানে বাতিলের পক্ষে হককে বিকৃত করা হচ্ছে। অবশ্য আমার বন্ধুরা আমার প্রবন্ধের মর্ম বা বক্তব্য বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন না তুললেও, সম্প্রতি ধর্মীয় চরমপন্থার বিরুদ্ধে যে প্রচারাভিযান চালানো হচ্ছে তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে তারা সংশয়ের আবর্তে দোল খাচ্ছেন। এই অভিযান আসলেই চরমপন্থাকে প্রতিহত করতে অথবা চরমপন্থীদের মধ্যপন্থার দিকে পরিচালিত করতে চায় কিনা সে ব্যাপারে তারা স্থির নিশ্চিত নন। তাদের আশংকা ইসলামী পুনর্জাগরণ একটি তাৎপর্যপূর্ণ রাজনৈতিক শক্তিতে রুপান্তরিত হওয়ার পূর্বে একে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করার জন্যে এসব প্রচারাভিযান শুরু করা হয়েছে। বন্ধুরা বলছেন, বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ন ইস্যুতে সরকারের বিরোধিতায় লিপ্ত হলেই সরকার ধর্মনিষ্ঠ তরুনদের প্রতি দৃষ্টি দিতে শুরু করেন। এর একটি প্রমাণ এই যে, ক্ষমতাসীন শাসকগোষ্ঠী আসলে গোঁড়া ধর্মীয় গ্রুপগুলোকে পৃষ্ঠপোষকতা দান করেন, উদ্দেশ্য অন্যান্য ইসলামী আন্দোলনের বিরুদ্ধে এদেরকে ব্যবহার করা। অত:পর তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়ে গেলে তারা ঐ ধর্মীয় গ্রুপগুলোকে উৎখাত করেন। এই হিসেবে বন্ধুদের যুক্তি হচ্ছে, কর্তৃপক্ষের ও ধর্মীয় গ্রুপগুলোর মধ্যেকার সংঘর্ষের কারণগুলো ধর্মীয় চরমপন্থা বা গোঁড়ামীর ভিত্তি হিসেবে খাড়া করা যায় না। তারা আরো মনে করেন যে, মুসলিম দেশগুলোর শাসকরা ইসলামী আন্দোলনকেই সবচেয়ে মারত্মক শত্রু হিসেবে গণ্য করেন। এরূপ কর্তৃপক্ষ চরম ডান অথবা চরম বামের সাথে আঁতাত গড়তে পারে, কিন্তু ইসলামী আন্দোলনের সাথে কখনো নয়।
কখনো কখনো তারা এই আন্দোলনের সাথে সংঘর্ষে অস্থায়ীভাবে বিরতি দেন আবার কখনো কখনো তাদের রাজনৈতিক ও আদর্শিক প্রতিপক্ষের সাথে সংঘাতের মধ্যে ইসলামী আন্দোলনকেও জড়িয়ে ফেলার অপচেষ্টা চালান। পরিশেষে কর্তৃপক্ষ ও প্রতিপক্ষ দেখতে পান যে, তাদের উদ্দেশ্য ও উপায়ের মধ্যে সাদৃশ্য আছে। অতএব ইসলামী আন্দোলনের বিরুদ্ধে তাদের আঁতাত গড়তে বিন্দুমাত্র বিলম্ব হয় না। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কুরআনুল কারীমে ঘোষণা করেছেন, “আল্লাহর মুকাবিলায় তারা তোমার কোন উপকার করতে পারবে না; যালিমরা একে অপরের বন্ধু; আর আল্লাহ্ তো মুত্তাকীদের বন্ধু।”(৪৫:১৯) বর্তমান ঘটনাবলীই এর সত্যতা বহন করে। মিসরে ইসলামী গ্রুপগুলোকে চরমপন্থী রূপ নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিল। কিন্তু ক্রমান্বয়ে তারা নরম ও মধ্যপন্থী দৃষ্টি গ্রহণ করতে শুরু করে। এর কৃতিত্ব অবশ্য বিভিন্ন মুসলিম চিন্তাবিদ ও ধর্মপ্রচারকদের প্রাপ্য। তারা ঐ গ্রুপগুলোকে ওপর তাদের চিন্তার প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হন। ফলত এখন অধিকাংশ ইসলামী গ্রুপের মধ্যে নরম ও মধ্যপন্থার লক্ষণগুলো স্পষ্ট হয়ে ওঠেছে। বিম্ময়ের ব্যাপার, চরমপন্থার প্রাধান্যের সময় ক্ষমতাসীনরা চুপচাপ ছিলেন; কিন্তু মধ্যপন্থী প্রবণতা জোরদার হওয়ার সাথে সাথে তারা ঐ গ্রুপগুলোকে নিশ্চিহ্ন করার জন্যে সর্বশক্তি নিয়োগ করেন।
এই হতাশাব্যঞ্জক পরিস্থিতি সম্পর্কে আমি যে অসতর্ক ছিলাম তা নয়, বরং এসব অবস্থা সামনে রেখেই ‘আল-আরাবী\'তে প্রকাশিত আমার প্রবন্ধের গোড়াতেই আমি লিখেছিলাম:
‘আল-আরাবী’ যে মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে ‘ধর্মীয় চরমপন্থার’ মত বিষয়ে আলোচনার আহবান জানিয়েছে তার গুরুত্ব আমি দ্বিধাহীন চিত্তে স্বীকার করি। এসত্ত্বেও সমসাময়িক ঘটনাবলীতে এর প্রতিক্রিয়ার কথা চিন্তা করে প্রথমে আমি বিষয়টি নিয়ে লেখার ব্যাপারে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলাম। বিশেষ করে আমার এই আশংকা ছিল যে, আমি যা কিছু লিখব তার অপব্যাখ্যা হতে পারে অথবা আমার কিংবা পত্রিকাটির ইচ্ছার বিপরীতে অন্য কোন উদ্দেশ্যে এর অপপ্রয়োগ হতে পারে।
বস্তুত বর্তমানে লেখক ও বক্তারা ধর্মীয় চরমপন্থাকে তাদের আক্রমণের লক্ষ্য বস্তুতে পরিণত করেছে। আমি দুর্বলের বিরুদ্ধে সবলের পক্ষ নিতে চাই না। আর এটাও সত্য যে, বিরোধী বা প্রতিপক্ষের তুলনায় ক্ষমতাসীন কর্তৃপক্ষ শক্তিশালী অবস্থানে থাকেন। বলাবাহুল্য, ইসলামপন্থীরা আত্মপক্ষ সমর্থনেরও অধিকার পান না। সংবাদ মাধ্যমে মত প্রকাশের স্বাধীনতা তো নেই-ই, এমনকি মসজিদের প্লাটফরমকেও এ উদ্দেশ্যে ব্যবহারের সুযোগ নেই।
আমার দ্বিধাদ্বন্দ্ব আরেকটি কারণে জোরদার হয়েছে যে, গত কয়েক দশক ধরে ইসলাম বিরোধীরা ইসলামপন্থীদের বিরুদ্ধে রাশি রাশি অভিযোগ উত্থাপন করে চলেছে। তাদেরকে প্রতিক্রিয়াশীল, গোঁড়া, শত্রু, বিদেশের দালাল ইত্যাদি অভিযোগে ‘ভূষিত’ করা হয়। অথচ কোন পর্যবেক্ষকেরই এটা বুঝতে বাকী থাকে না যে, পূর্ব ও পশ্চিমের উভয় পরাশক্তি বলয় ইসলামপন্থীদের প্রতি বৈরী মনোভাব পোষণ করে এবং তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করার সকল সুযোগের অপেক্ষায় থাকে।
যা হোক, অনেক চিন্তা-ভাবনার পর আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, বিষয়টি একটি বিশেষ দেশের নয় বরং সারা মুসলিম জাহানের সমস্যা। নীরবতা অবলম্বন করলেই বিষয়টির নিষ্পত্তি হবে না। আলোচনায় শামিল না হওয়াটাই বরঞ্চ জিহাদের ময়দান থেকে পলায়নের মতোই অনৈসলামী কাজ। সুতরাং আমি নিজেকে আল্লাহ কাছে সোপর্দ করে প্রকৃত সত্য প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলি। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) একটি হাদীসে বলেছেন: ‘নিয়তের ওপরই কর্মের ফলাফল নির্ভর করে এবং প্রত্যেক ব্যক্তি সেই ফলই পাবে যার নিয়ত সে করেছে।” (বুখারী ও মুসলিম)
অনেক লেখক অজ্ঞতাবশত অথবা উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে কিংবা বিষয়টির প্রকৃতি সম্পর্কে অগভীর ধারণার দরুন মুক্তকচ্ছের মতো বক্তব্য রেখে গেছেন। এমতাবস্থায় এই অভিযানে অংশ নিয়ে মুসলিম চিন্তাবিদদের সত্য প্রকাশে ব্রতী হওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না।
তাছাড়া ধর্মীয় চরমপন্থা বিষয়টির প্রতি আমার দীর্ঘদিনের আগ্রহ আমার সংকল্পকে আরো জোরদার করেছে। কয়েক বছর আগে আমি তাকফীরের (কাউকে কাফির ঘোষণার প্রবণতা) বাড়াবাড়ি সম্পর্কে ‘আলমুসলিমুল মুয়াসির’ পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লিখেছিলাম। “মুসলিম তরুণদের পুনর্জাগরণ” শীর্ষক আমার আরেকটি প্রবন্ধ ‘আল-উম্মাহ’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। আমি যখনি মুসলিম তরুণদের সাথে মুখোমুখী কিংবা শিবির ও সেমিনারে আলোচনার সুযোগ পেয়েছি তখনি তাদেরকে মধ্যপন্থার প্রতি আহবান জানিয়েছি এবং বাড়াবাড়ির পরিণাম সম্পর্কে হুঁশিয়ার করে দিয়েছি। অবশ্য ‘আল-আরাবী\'তে যে প্রবন্ধটি লিখেছিলাম তা ছিল সুনির্দিষ্ট বিষয়ের ওপর একটি ফরমায়েশী লেখা।
এসব কাণে আমি বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার তাগিদ অনুভব করি। বিশেষত ধর্মীয় চরমপন্থার বাস্তবতা, কারণ ও প্রতিকার প্রসঙ্গে বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা হওয়া দরকার এবং তা হওয়া দরকার ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে। যারা বিষয়টিকে বিকৃত ও অসদুদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে চায় তাদের তৎপরতা সত্ত্বেও আমি এগিয়ে যেতে সংকল্পবদ্ধ। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন: “মধ্যপন্থীরা এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্ম পর্যন্ত জ্ঞানের পতাকা বহন করে নিয়ে যাবে। তারাই জ্ঞানকে বিকৃতি ও অপব্যাখ্যার হাত থেকে রক্ষা করবে।”
হাদীসটি এই ইঙ্গিত দেয় যে, আল্লাহর ক্রোধ থেকে বাঁচার জন্যে বিজ্ঞ ব্যক্তিদেরকে সত্য গোপন নয়, প্রকাশ করার দায়িত্ব পালন করতে হবে। অতএব যারা বিষয়টির সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত তাদেরকেও এ দায়িত্ব পালন করা উচিত। বাড়াবাড়ির জন্যে কেবল তরুণদের দায়ী করা সঙ্গত নয়। যারা ইসলামের শিক্ষা পালনে ঔদাসীন্য প্রদর্শন করেন অথচ নিজেদেরকে নির্দোষও ভাবেন তারাও সমভাবে দায়ী। নামধারী মুসলমানরা- তা পিতামাতা, শিক্ষক-পন্ডিত অথবা যে কেউ হোন- নিজ নিজ দেশেই ইসলাম, ইসলামপন্থী ও ইসলাম প্রচারকদেরকে প্রায় অস্পৃশ্য করে রেখেছেন। এটা আশ্চর্যের ব্যাপার, আমরা চরমপন্থার সমালোচনায় সোচ্চার হয়ে উঠি, কিন্তু আমাদের নিজস্ব গোঁড়ামি অর্থাৎ ধর্মীয় বিধি-বিধান পালনে অবহেলা ও শিথিলতার প্রশ্নে নির্বিকার। আমরা তরুণদেরকে গোঁড়ামি ও বাড়াবাড়ি পরিহার করার উপদেশ দিই এবং তাদেরকে নমনীয় ও সুবিবেচক হতে বলি, কিন্তু প্রবীণদেরকে কখনো বলি না যে, আপনারাও মুনাফেকী, মিথ্যাচার, প্রতারণা তথা সর্বপ্রকার স্ববিরোধিতা থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করুন। আমরা তরুণদের কাছ থেকে সব কিছু দাবী করি, কিন্তু তাদেরকে যা নসিহত করি নিজেরা তা পালন করি না, যেন সব অধিকার আমাদের আর কর্তব্যের দায়ভার সবটাই যেন তরুণদের। অথচ দায়িত্ব ও কর্তব্য সকলের ওপর সমানভাবে প্রযোজ্য। আজ আমাদের যা প্রয়োজন তা হচ্ছে, প্রচন্ড সাহস সঞ্চয় করে আমাদের স্বীকার করতে হবে যে, আমাদের নিজেদের দুষ্কর্মের দরুনই তরুণরা ধর্মীয় চরমপন্থার আশ্রয় নিয়েছে। আমরা কুরআন তিলাওয়াত করি, কিন্তু এর আহকাম মেনে চলি না, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)- এর প্রতি ভালবাসার দাবী করি, কিন্তু কার্যত তাঁর সুন্নাহ পালন করি না। আরো মজার ব্যাপার আমারা ইসলামকে রাষ্ট্র ধর্ম বলে ঘোষণা করি, কিন্তু আইন-কানুন প্রণয়নের সময় ইসলামের নাম গন্ধ খুঁজে পাওয়া যায় না। প্রকৃতপক্ষে আমাদের স্ববিরোধী ও মুনাফেকী আচরণের জন্যেই তরুণরা আমাদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজেরাই ইসলামকে বোঝার চেষ্টা করছে। কেননা, তাদের দৃষ্টিতে পিতামাতাদের অবস্থা হতাশাব্যঞ্জক। আলিমরা উদাসীন, শাসকরা বৈরী আর পরামর্শদাতার ছিদ্রান্বেষী। অতএব তরুণদের প্রতি শান্ত, সংযত ও সুবিবেচক হওয়ার উপদেশ দেয়ার আগে আমাদের নিজেদেরকে ও সমাজকে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী সংস্কার করতে হবে। চরমপন্থা নির্মূল ও তরুণদের মধ্যে ইসলামী পুনর্জাগরণেকে সঠিক খাতে প্রবাহিত করার ব্যাপারে সরকারী ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্তব্য ও ভূমিকার প্রতি কর্তৃপক্ষ ও চিন্তাশীল লেখকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।
অনেকে মনে করেন, সকল প্রকার চরমপন্থা ও বিচ্যুতিসহ যা কিছু ঘটেছে বা ঘটে চলেছে তার জন্যে সরকারী ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোই দায়ী। বস্তুত এই প্রতিষ্ঠানগুলোর গুরুত্ব অনস্বীকার্য হলেও এদের ওপর আরোপিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনে তারা অক্ষম; কেননা ক্ষমতাসীন কর্তৃপক্ষ তাদের নীতির প্রতি প্রশংসা ও সমর্থন আদায়ের মতলবে এসব প্রতিষ্ঠানকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেন। অথচ সকলে একথা স্বীকার করবেন যে, মুসলিম বিশ্বের এই ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো সরকারী হস্তক্ষেপমুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ পেলে তরুণদের পথ নির্দেশ ও জ্ঞান প্রদানের ক্ষেত্রে অবশ্যই ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে পারে। কিন্তু এই স্বাধীনতার অভাবে এগুলো প্রানহীন কংকালে পর্যবসিত হয়েছে।
আবার এটাও আমাদেরকে স্মরন রাখতে হবে যে, উপদেষ্টাদের প্রতি যদি তরুণদের আস্থা না থাকে তবে সেসব উপদেষ্টার উপদেশ অর্থহীন। পারষ্পরিক আস্থা না থাকলে প্রতিটি উপদেশ বাগাড়ম্বরের নামান্তর। প্রকৃতপক্ষে সরকার নিযুক্ত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে শরীয়তের শিক্ষার যে যথার্থ প্রতিফলন ঘটে না তা মনে করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। এগুলো আসলেই সরকারের হাতের ক্রীড়নক মাত্র। তারা যদি সত্যিকার অর্থে সমাজে তাদের প্রভাব রাখতে চায় তবে সর্বপ্রথম তাদের ঘরকেই আগে সাজাতে হবে। এজন্যে তাদেরকে সদা অস্থির রাজনৈতিক কুচক্রের মধ্যে জড়িয়ে পড়া চলবে না। তাদের প্রধান কাজ হবে এমন এক দল ফকীহ গড়ে তোলা যারা হবে ইসলাম সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের অধিকারী ও যুগসচেতন অর্থাৎ কুরআনের ভাষায় “যারা আল্লাহর বাণী পৌঁছিয়ে দেয় এবং তাঁকে ছাড়া আর কাউকে ভয় করে না।” (৩৩ : ৩৯) বস্তুত আমাদের বর্তমান সমাজে এরূপ অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন সৎ মনীষীর প্রয়োজন অনস্বীকার্য। কেবল এরাই ইসলামী পুনর্জাগরণের লক্ষ্যে তরুণ সমাজকে সঠিক পথ নির্দেশ দিতে পারেন। যেসব লোক ইসলামী পুনর্জাগরণ থেকে দূরে সরে আছেন অথবা এর আশা-আকাঙ্খা উপলব্দি না করে এবং হতাশা ও দুর্ভোগের অংশীদার না হয়েই কেবল সমালোচনা করে চলেছেন তারা কখোনোই এই আন্দোলনের ইতিবাচক অবদান রাখতে পারে না। আমাদের একজন প্রাচীন কবি লিখেছেন : “যারা নিঃস্বার্থ যাতনা ভোগ করে তারা ছাড়া আর কেউ তীব্র আকাঙ্খার তীক্ষ্ম বেদনা উপলব্ধি করতে পারে না।” ইসলামের প্রচার ও প্রসারে যাদের হৃদয়ে আকাঙ্খা নেই তারা আসলেই আত্মকেন্দ্রিক আর এসব লোকের কোনো অধিকার নেই ইসলাম অনুরাগীদের ভুল ধরার অথবা তাদের সংশোধনের জন্যে নসিহত করার। যদি তারা গায়ের জোরে এই অধিকার প্রয়োগ করতে চায় তাহলে কেউ তাদের কথায় কর্ণপাত করবে না।
উপসংহারে, আমার পরামর্শ হচ্ছে যারা তরুণদের উপদেশ দিতে আগ্রহী তাদেরকে পাণ্ডিত্যাভিমান পরিহার করে আইভরি টাওয়ার থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। ধুলির ধরণীতে নেমে এসে তরুণদের সাথে মিশতে হবে। যুব সমাজের আশা-আকাঙ্খা, সংকল্প, উদ্দীপনা ও সৎ কর্মগুলোর যথাযথ মূল্যায়ণপূর্বক তাদের ইতিবাচক ও নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য করতে হবে যাতে তাদেরকে সঠিক দিক নির্দেশনা দেয়া যায়।
ড. ইউসুফ আল-কারজাভী
বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম
প্রথম অধ্যায়
অভিযোগ ও বাস্তবতা
কোন বিষয়ে স্বচ্ছ ধারণা না থাকলে সে বিষয়ে মতামত প্রকাশ করা সমীচীন নয়। তাই যুক্তিবাদীরা মনে করেন অজ্ঞাত ও অস্পষ্ট বিষয় মত প্রকাশ করা উচিত নয়।
সুতরাং ধর্মীয় গোঁড়ামী ও চরমপন্থাকে আমাদের উক্ত প্রেক্ষিতেই বিচার করতে হবে। এর ভাল বা মন্দ বিচারের আগে এর প্রকৃত তাৎপর্য জানতে হবে। এজন্যে সর্বাগ্রে প্রয়োজন এর বাস্তবতা ও বৈশিষ্ট্যগুলোর বিশ্লেষণ। আক্ষরিক অর্থে, উগ্রতাবাদ বা চরমপন্থার অর্থ হচ্ছে কেন্দ্র থেকে সম্ভাব্য সর্বশেষ প্রান্তে অবস্থান। বাহ্যত, এটা ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ, চিন্তাধারা তথা আচার-আচরণের ক্ষেত্রে অনুরূপ দূরত্বে অবস্থানের দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করে। চরমপন্থার একটি অন্যতম পরিণাম হচ্ছে এটি সমাজকে বিপজ্জনক ও নিরাপত্তাহীন পরিস্থিতির দিকে ঠেলে দেয়। অথচ ঈমান, ইবাদত, আচার-আচরণ, আইন-বিধি তথা জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইসলাম মধ্যম সুষমপন্থা অবলম্বনের সুপারিশ করেছে। এটাকেই আল্লাহ তায়ালা ‘সিরাতুল মুস্তাকীম’ বা সহজ সরল পথ বলে উল্লেখ করেছেন। এ পথের একটি সুনির্দিষ্ট ও সুষ্পষ্ট বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এর বিপরীত যতো মত পথ রয়েছে তার অনুসারীরা আল্লাহর গযবে পতিত হয়েছে। মোটকথা, আল্লাহ নির্দেশিত সিরাতুল মুস্তাকীমই হচ্ছে সুপথ আর এর উল্টো পথই হচ্ছে কুপথ বা বিপথ। তাই মধ্যম বা ভারসাম্যময় পন্থা ইসলামের কেবল সাধারণ বৈশিষ্ট্য নয় বরং এর মধ্যেই ইসলামের মৌলিক পরিচয় নিহিত। এ প্রসঙ্গে কুরআনের ঘোষণা:
“এমনিভাবে আমরা তোমাদেরকে একটি মধ্যপন্থী উম্মাহ হিসেবে সৃজন করেছি যাতে তোমরা মানব জাতীর জন্যে সাক্ষী হবে আর রাসূল (সা) তোমাদের জন্যে সাক্ষী হবেন।” (২: ১৪৩)
এই দৃষ্টিতে,মুসলিম উম্মাহ একটি সুবিচারপূর্ণ ও ভারসাম্যপূর্ণ পন্থার পথিক। একইভাবে এই জাতি ইহলৌকিক ও পরলৌকিক জীবনে সরল পথ থেকে মানুষের প্রতিটি বিচ্যুতির বিরুদ্ধে সাক্ষী। ইসলামে এমন কিছু পরিভাষা রয়েছে যাতে মধ্যপন্থা অবলম্বনের এবং সব ধরনের চরমপন্থা ও হঠকারিতা প্রত্যাখ্যান ও পরিহারের আহবান জানানো হয়েছে। যেমন গুলু (বাড়াবাড়ি), তানাতু (উদ্রতা) ও তাশদীদ (কঠোরতা) -এই পরিভাষাগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ইসলাম বাড়াবাড়িতে শুধু নিরুৎসাহিত করেনি বরং এর বিরুদ্ধে কঠোর হুঁসিয়ারী উচ্চারণ করেছে। নিম্নোক্ত হাদীসগুলোতে এর সত্যতা পাওয়া যায়।
১. “ধর্মে বাড়াবাড়ি সম্পর্কে সাবধান! তোমাদের পূর্ববর্তী (জাতিগোষ্ঠি) এরূপ বাড়াবাড়ির পরিণামে নিশ্চিহ্ন হয়েছে।” (আহমাদ, নাসাই ও ইবনে মাজাহ) এখানে জাতি বলতে অন্যান্য ধর্মাবলম্বী জাতিগোষ্ঠিকে বোঝানো হয়েছে।” এর মধ্যে আহলে কিতাব বিশেষত খ্রীষ্টানরা উল্লেখযোগ্য। এদেরকে সম্বোধন করে আল-কুরআন বলছে: “বলুন, হে আহলে কিতাব! তোমরা তোমাদের দ্বীন সম্বন্ধে অন্যায় বাড়াবাড়ি করো না; এবং যে-সম্প্রদায় অতীতে বিপথগামী হয়েছে এবং অনেককে বিপথগামী করেছে এবং সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে তাদের স্বেচ্ছাচারিতার অনুসরণ করো না”। (৫:৭৭)
উপরোক্ত কারণে মুসলমানদেরকে বিপথগামীদের পথ অনুসরণ থেকে বিরত থাকার কঠোর তাগিদ দেয়া হয়েছে। যারা অন্যের ভুলভ্রান্তি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে প্রকৃতপক্ষে তারাই অধিকতর সুখী। তদুপরি বাড়াবাড়ি বা সীমালংঘন (আল-গুলু) এমন অর্থহীন কর্মকান্ডে প্ররোচিত করে যার তান্ডব আমাদের অগোচরে বিস্তৃত হয়ে শেষ পর্যন্ত গোটা সমাজদেহকে একটা হুমকির মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়। হযরত মুহাম্মদ (সা:) বিদায় হজ্জের সময় মুজদালিফায় পৌঁছে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) কে কিছু প্রস্তরখন্ড সংগ্রহ করতে বললেন। ইবনে আব্বাস (রা) কিছু প্রস্তর খন্ড সংগ্রহ করে আনলেন। রাসুলুল্লাহ (সা) পাথরগুলোর আকার দেখে সন্তোষ প্রকাশ করে বললেন: “হ্যাঁ, এই পাথরগুলোর মতোই ধর্মীয় ব্যাপারে বাড়াবাড়ি বা জবরদস্তি থেকে সাবধান।” (ইমামা আহমাদ, আন-নাসাই, ইবনে কাছীর ও হাশীম) এ থেকে এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, মুসলমানরা যেন অতি উৎসাহী হয়ে বড় পাথর ব্যবহারের মতো বাড়াবাড়িতে প্রবৃত্ত না হয়। ইমাম ইবনে তাইমিয়াও ঈমানের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল ক্ষেত্রে তথা ইবাদত ও লেনদেনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ির বিরুদ্ধে সতর্ক করে দিয়েছেন। তিনি খ্রীষ্টানদেরকে বিশ্বাস ও আচরণের ব্যাপারে সবচেয়ে সীমালংঘনকারী জাতি হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ পাকও কুরআনুল কারীমে তাদেরকে ভৎসনা করে বলেছেন, “ধর্মীয় বিষয়ে তোমরা সীমালংঘন করো না” (৪:১৭১)
২. “তারা অভিশপ্ত, যারা চুল ফাঁড়তে (অর্থাৎ ক্ষুদ্র বিষয়ে) লিপ্ত এবং রাসুলূল্লাহ (সা) তিনবার এই কথা উচ্চারণ করলেন।”(মুসলিম, আহমাদ ও আবু দাউদ) ইমাম আননববী বলেন, “এখানে ‘চুল ফাঁড়তে’ লিপ্ত ব্যক্তিদের বলতে তাদের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যারা কথায় ও কাজে সীমা অতিক্রম করে।” উল্লিখিত দু’টি হাদীসে স্পষ্টত এ কথাই ব্যক্ত করা হয়েছে যে, বাড়াবাড়ি ও হঠকারিতার পরিণামে মানুষ সম্পূর্ণরূপে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক ক্ষতির সম্মুখীন হবে।
৩. রাসুলুল্লাহ (সা) বলতেন, “নিজের ওপর এমন অতিরিক্ত বোঝা চাপিও না যাতে তোমার ধ্বংস হওয়ার আশঙ্কা থাকে। তোমাদের পূর্ববর্তী জনগোষ্ঠী নিজেদের ওপর অতিরিক্ত বোঝা চাপিয়ে ধ্বংস হয়েছে। তাদের ধ্বংসাবশেষ পুরাতন মঠ-মন্দিরে খুঁজে পাওয়া যায়।” আবু ইয়ালা তার মসনদে আনাস ইবনে মালিকের বরাতে এবং ইবনে কাছীর সূরা হাদীদের ২৭ আয়াতের তাফসীরে এই হাদীস উল্লেখ করেছেন। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা) সর্বদা ধর্মীয় বাড়াবাড়ির প্রবণতাকে প্রতিহত করতে চেয়েছেন। তিনি তাঁর সাহাবীদের মধ্যে যাদেরকে ইবাদত-বন্দেগীতে বাড়াবাড়ি করতে দেখেছেন, সংসার ধর্ম পালনে বিমুখ দেখেছেন তাদেরকে প্রকাশ্যে ভৎসনা করেছেন। কারণ এসবই হচ্ছে ইসলামের মধ্যপন্থার পরিপন্থী। ইসলাম দেহ ও আত্মার সুষম বিকাশ চায় অর্থাৎ মানুষের পূর্ণরূপে বেঁচে থাকার অধিকার এবং স্রষ্টাকে উপাসনা করার অধিকারের মধ্যে সমন্বয় চায়। মানুষের অস্তিত্বের যৌক্তিকতা এখানেই।
এই আলোকে মানুষের আত্মিক পরিশুদ্ধি এবং ব্যক্তিগতভাবে ও সমষ্টিগতভাবে তার নৈতিক ও বৈষয়িক উৎকর্ষের লক্ষ্যে ইসলাম ইবাদতের সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি নির্ধারণ করে দিয়েছে। এভাবে ইসলাম এমন এক সমাজ গড়তে চায় যেখানে ভ্রাতৃত্ব ও সম্প্রীতি বিরাজ করবে এবং এটা করতে গিয়ে ইসলাম সমাজ, সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশে বাধা সৃষ্টি করে না। তাই দেখা যায় নামাজ, রোজা ও হজ্জের মতো ফরজ ইবাদতগুলোর একই সাথে ব্যক্তিগত ও সামাজিক ভূমিকা রয়েছে। স্বভাবত এই দায়িত্বগুলো পালন করতে গিয়ে একজন মুসলমান জীবনের মূলস্রোত থেকেও বিচ্ছিন্ন হয় না আবার সমাজ থেকেও তাকে নির্বাসিত হতে হয় না। বরং ভাবগত ও বাস্তব ও উভয় দিক দিয়ে সমাজের সাথে তার সম্পর্ক আরো ঘনিষ্ট হয়। এ কারণে ইসলাম বৈরাগ্যবাদকে অনুমোদন করে না। আর বৈরাগ্যবাদ মানে সমাজ থেকে নির্বাসন। সেখানে স্বাভাবিক সামাজিক জীবনের স্পন্দন থাকে না। ইসলাম চায়, এই স্বভাবসম্মত সামাজিক জীবন যাপনের মাধ্যমে মানুষ পবিত্রতা অর্জন করুক। সমাজের উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে প্রতিটি মানুষ তার অবদান রাখুক। অর্থাৎ ইসলামের দৃষ্টিতে গোটা পৃথিবী মানুষের ধর্মীয় কর্মকান্ডের ক্ষেত্র। তাই সিরাতুল মুস্তাকীমের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ মানুষের প্রতিটি কাজই ইবাদত ও জিহাদ বলে গণ্য করা হয়। ইসলাম অন্যান্য ধর্ম ও দর্শনের মতো মানুষের জৈবিক চাহিদাকে অস্বীকার করে তথাকথিত আধ্যাত্মিক সাধনায় তাকে মোটেও উৎসাহিত করে না। দেহের দাবীকে অস্বীকার বা উপেক্ষা করে আত্মার পরিশুদ্ধির স্থান ইসলামে নেই। এ ব্যাপারে কুরআনের ঘোষনা দ্ব্যর্থহীন: “হে আল্লাহ, আমাদের ইহকালকে সুন্দর করুন এবং সুন্দর করুন আমাদের পরকালকে।” (২:২০১)
হাদীসেও আমরা একই বাণীর প্রতিধ্বনি শুনতে পাই: “হে আল্লাহ, আমার সকল কাজকর্মের হিফাযতকারী ধর্মকে সঠিকরূপে উপস্থাপিত করুণ; আমার জাগতিক কর্মকান্ডকে পরিশুদ্ধ করুণ যেখানে আমি জীবন নির্বাহ করি এবং আমার পরকালীন জীবনকেও পবিত্র করুণ এবং সার্বিক কল্যাণের লক্ষ্যে আমার জীবনকে প্রাচুর্যের উৎস বানিয়ে দিন এবং সকল অপকর্ম থেকে আমাকে রক্ষা করে আমার মৃত্যুকে শান্তির উৎসে পরিণত করুন।” (মুসলিম)
হাদীসে আরো বলা হয়েছে :\"তোমার ওপর তোমার দেহের অধিকার রয়েছে।” (সকল প্রামাণ্য সূত্রে সমর্থিত) তদুপরি কুরআনুল কারীমে পরিচ্ছন্নতা ও সৌন্দর্যকে উপেক্ষা করার প্রবণতা অনমোদন করা হয়নি বরং এটাকে বান্দার প্রতি আল্লাহর দান বলে উল্লেখ করা হয়েছে। মক্কায় অবতীর্ণ একটি আয়াতে আল্লাহ পাক বলছেন:“হে আদমের সন্তানেরা! সুন্দর পরিচ্ছদে ভূষিত হও সব সময় এবং নামাযের স্থানেও। খাও ও পান করো কিন্তু অপচয় করো না। আল্লাহ অপচয়কারীকে ভালবাসেন না।”
“বলুন, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জীবিকা সৃষ্টির জন্যে যেসব শোভন বস্তু এবং বিশুদ্ধ ও পবিত্র জীবিকা সৃষ্টি করেছেন তাকে কে নিষিদ্ধ করেছে?” (৭:৩২)
মদিনায় অবতীর্ণ একটি সূরায় আল্লাহ তায়ালা বিশ্বাসীদের সম্বোধন করে বলেছেন : “হে ঈমানদাররা! আল্লাহ তায়ালা যেসব উৎকৃষ্ট বস্তু তোমাদের জন্যে হালাল করেছেন তাকে তোমরা হারাম করো না এবং সীমালংঘন করো না। আল্লাহ সীমালংঘনকারীকে পছন্দ করেন না। আল্লাহ তোমাদেরকে যে হালাল ও উৎকৃষ্ট জীবিকা দিয়েছেন তা থেকে আহার করো আর আল্লাহকে ভয় করে চলো যাঁর প্রতি তোমরা ঈমান এনেছ।” (৫:৮৭-৮৮)
এসব আয়াতে ঈমানদারদের কাছে পবিত্রতা অর্জনের প্রকৃত ইসলামী পথ বাতলে দেয়া হয়েছে এবং অন্যান্য ধর্মে যেসব বাড়াবাড়ি রয়েছে সেরূপ প্রবণতা থেকে মুসলমানদেরকে নিবৃত করা হয়েছে। এই আয়াত দু’টির শানে নুযূলও এখানে লক্ষণীয়। একদল সাহাবী নিজেদেরকে খোজা করে দরবেশ হয়ে ঘুরে বেড়ানোর ইচ্ছে ব্যক্ত করলে এই আয়াত নাযিল হয়।
ইবনে আব্বাস (রা) বলেন: “একটি লোক রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে এসে বললেন: “হে আল্লাহর রাসূল, আমি যখনি এই গোশত গুলো খাই তখুনি আমার কামপ্রবৃত্তি মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে, তাই আমি গোশত না খাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।” এবং এরপর পরই আয়াত নাযিল হয়। আনাস ইবনে মালিক (রা) বর্ণনা করেন, “একদল লোক নবী সহধর্মিণীদের কাছে এসে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর এবাদত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। এ ব্যাপারে অবহিত হওয়ার পর তারা তাদের ইবাদত-বন্দেগীকে অপর্যাপ্ত বিবেচনা করে একজন বললেন, আমি সর্বদা সারারাত নাময পড়ব; আরেকজন বললেন, আমি সারা বছর রোজা রাখব এবং কখনো ভাঙ্গবো না। এ সময় আল্লাহর নবী তাদের কাছে এলেন এবং বললেন: “আল্লাহর শপথ আল্লাহর প্রতি আনুগত্য আমারই সবচেয়ে বেশী এবং তাঁকে বেশী ভয় করি তোমাদের চেয়ে; তথাপি আমি রোযা রাখি এবং ভাঙ্গিও, আমি ঘুমোই এবং নারীকে বিয়ে করি। সুতরাং যে আমার সুন্নাহকে অনুসরণ করে না সে আমার অনুসারীদের অন্তর্ভূক্ত নয়।”
প্রকৃতপক্ষে রাসূলুল্লাহ (সা) -এর সুন্নাহর মধ্যেই ইসলামের ধ্যান ধারণা এবং তার বাস্তব রূপায়নের সমগ্র চিত্র ফুটে উঠেছে। এতে আল্লাহর প্রতি, পরিবারের প্রতি, নিজের প্রতি, তথা প্রতিটি ক্ষেত্রে দায়িত্ব ও কর্তব্যের এক সুষম ও সমন্বিত রুপ মূর্ত হয়েছে।
ধর্মীয় চরমপন্থার ত্রুটি
বস্তুত সকল উগ্রতা ও বাড়াবাড়ির মধ্যে মারাত্মক ত্রুটি অন্তর্নিহিত থাকে। এ কারণে এর বিরুদ্ধে সতর্কতা বাঞ্ছনীয়। প্রথম ত্রুটি হচ্ছে সাধারণ মানবীয় প্রকৃতি বাড়াবাড়ির (excessivenes) সাথে সামঞ্জস্যশীল নয়; এই প্রকৃতি কোনো বাড়াবাড়িকে বরদাশত করতে পারে না। যদি মুষ্টিমেয় লোক স্বল্প সময়ের জন্যেও বাড়াবাড়ি সহ্য করতে পারে বৃহত্তর জনগোষ্ঠী তা করতে সক্ষম হবে না। আল্লাহর বিধান সমগ্র মানুষের জন্যে, মুষ্টিমেয় হঠকারীর জন্যে নয় যাদের তথাকথিত সহন ক্ষমতা বেশি বলে আপাতত প্রতীয়মান হয়। একবার রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর একজন বিশিষ্ট সাহাবী মুয়াযের ওপর ক্রদ্ধ হয়েছিলেন। কারণ তিনি নামাযের ইমামতিতে দীর্ঘ সময় ক্ষেপণ করেছিলেন বলে একজন মুসল্লী অভিযোগ করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে বললেন: “হে মুয়ায! তুমি কি মুসল্লীদের পরীক্ষা করছ? তিনি তিনবার এ কথার পুনরুক্তি করলেন।” (বুখারী) আরেকবার মহানবী (সা) অস্বাভাবিক ক্রুদ্ধ হয়ে একজন ইমামকে লক্ষ্য করে বললেন, “তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ ভাল কাজের (নামায) প্রতি মানুষের বিতৃষ্ণা সৃষ্টি কর। তাই তোমরা যখনি নামায পড়াবে তখন তা সংক্ষিপ্ত করা উচিত, কারণ মুসল্লীদের মধ্যে দুর্বল ও বৃদ্ধ এবং কর্মব্যস্ত লোক থাকে। ” (বুখারী) রাসুলুল্লাহ (সা) মুয়ায ও আবু মূসাকে ইয়ামানে প্রেরণের প্রাক্কালে এই উপদেশ দিয়েছিলেন:“(জনগণের কাছে ধর্মীয় বিষয়গুলো) সহজ করে তুলে ধরো, কঠিনরূপে নয়। একে অপরকে মান্য করো, বিভেদে লিপ্ত হয়ো না।” (সকল প্রামাণ্য সূত্রে সমর্থিত)
উমর ইবনে খাত্তাব (রা) এর ওপর জোর দিয়ে বলেছেন: “নামাযের ইমামতিতে দীর্ঘসূত্রিতা করে বান্দার কাছে তার কাজকে (আমল) এবং আল্লাহকে ঘৃণার পাত্রে পরিণত করো না”।
বাড়াবাড়ি দ্বিতীয় ত্রুটি হচ্ছে, এটি ক্ষণস্থায়ী। যেহেতু মানুষের সহ্য ক্ষমতা ও অধ্যবসায় স্বভাবত সীমিত তাই সহজে সে একঘেঁয়েমি অনুভব করে। দীর্ঘ সময় ধরে বাড়াবাড়িমূলক ক্রিয়াকর্মে লিপ্ত থাকা তার স্বভাব বিরুদ্ধ। এমন একটা সময় আসবে যখন সে ক্লান্ত হয়ে পড়বেই, দৈহিক ও মানসিক উভয় দিক দিয়ে। এমনকি স্বভাবসম্মত নূন্যতম কাজটিও সে পরিত্যাগ করবে। অথবা অতিরিক্ত আমলের উল্টো এমন এক পথ বেছে নেবে যা হবে শেষ পর্যন্ত চরম অবহেলা ও শৈথিল্যের শামিল। এমন কিছু লোকের সাথে আমার সাক্ষাৎ ঘটেছে যাদেরকে দৃশ্যত গোঁড়া ও কঠোর মনে হয়েছে। পরে আমি তাদের সম্পর্কে খোঁজ খবর নিয়ে জেনেছি যে, তারা হয় পথভ্রষ্ট হয়ে সম্পূর্ণ বিপরীত পথে চলতে শুরু করেছে কিংবা ন্যূনপক্ষে হাদীসে বর্ণিত হঠকারী চরিত্রের লোকদের মতো সবেগে পিছু হটে এসেছে। এ সম্পর্কিত হাদীসটি হচ্ছে: “যে (হঠকারী জল্লাদবাজ লোক) (নির্দিষ্ট) দূরত্বও অতিক্রম করতে পারে না এমনকি পারে না তার বাহনের পিঠটাকেও ঠিক রাখতে।” (জাবিরের সনদে আল-বাজ্জাজ)
রাসূলুল্লাহর (সা) আরেকটি হাদীসেও এরূপ ইঙ্গিত রয়েছে: “সেই সব সৎকর্মে প্রবৃত্ত হও যা সহজে সম্পন্ন করা যায়; কেননা আল্লাহ তায়ালা (পুরষ্কার দানে) ক্লান্ত হন না যতোক্ষণ না তুমি (নেক আমলে) ক্লান্ত ও অবসন্ন হও... এবং আল্লাহর কাছে সেই আমলই সবচেয়ে প্রিয় যা নিয়মিত সম্পাদন করা হয় তা যতই ছোট হোক না কেন।” (হযরত আয়েশার (রা) বরাতে বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ ও আন-নাসাঈ) ইবনে আব্বাস (রা) বলেন: “মহানবী (সা) -এর একজন সেবক দিনে রোযা রাখতেন আর সারা রাত নামায পড়তেন। রাসূলুল্লাহ (সা) কে এ বিষয়ে জানান হলে তিনি বললেন, “প্রতিটি কাজের একটি শীর্ষ বিন্দু থাকে এবং তাকে অনিবার্যভাবে অনুসরণ করে শৈথিল্য। যে তার স্বাভাবিক সরল জীবনে আমার সুন্নাহকে অনুসরণ করে সে সঠিক পথে আছে আর যে শৈথিল্যের কারণে অন্যের পথ নির্দেশ অনুসরণ করে সে (ভুল করল) এবং (আল্লাহ পাক প্রদত্ত সরল পথ থেকে) বিচ্যুত হলো।” (আল বাজ্জাজ)
আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বলেন: “ইবাদত-বন্দেগীতে লিপ্ত থাকতে থাকতে ক্লান্ত ব্যক্তিদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা) কে অবহিত করা হলে তিনি বললেন: ‘এটা হচ্ছে ইসলামের কঠোর অনুশীলন এবং আমলের সর্বোচ্চ পর্যায়। প্রতিটি গোঁড়া ক্রিয়াকলাপের একটি শীর্ষ পর্যায় থাকে এবং সেই সাথে থাকে অনিবার্য শৈথিল্য.. যার সহজ-সরল আমল কিতাব (কুরআনুল কারীম) ও সুন্নাহর আলোকে নিষ্পন্ন হয় সে-ই সঠিক পথের ওপর কায়েম থাকে আর যার অবসন্নতা অবাধ্যতায় পর্যবসিত হবে তার ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী।” (আহমাদ এবং আবু শাকির সমর্থিত)
ইবাদতের ক্ষেত্রে চরমপন্থা বর্জনের এবং মধ্যপন্থা অবলম্বনের কী চমৎকার তাগিদ এই হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) মুসলমানদেরকে দিয়েছেন! তিনি আরো বলেছেন: “ধর্ম খুব সহজ আর সে নিজের ওপর অতিরিক্ত বোঝা চাপিয়ে নেয় সে তা শেষ পর্যন্ত ধরে রাখতে পারে না। সঠিক পথে চলো (বাড়াবাড়ি বা অবহেলা কোনটাই না করে), (পূর্ণতার) নিকটবর্তী হওয়ার চেষ্টা করো এবং (তোমার সৎকর্মের পুরষ্কার লাভের জন্যে) সুসময়ের অপেক্ষা করো।” (বুখারী ও নাসাঈ, আবু হুরায়রা বর্ণিত)
তৃতীয়ত, হঠধর্মী বাড়াবাড়ি অন্যের অধিকার ও কর্তব্যকে বিপন্ন করে। এ প্রসঙ্গে একজন বুযুর্গ বলেন: “প্রত্যেক বাড়াবাড়ির মধ্যে কারো কারো অধিকার হারানোর বেদনা জড়িত আছে।” আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) ইবাদত-বন্দেগীতে এমন মশগুল থাকতেন যে, তার স্ত্রীর প্রতি কর্তব্যও উপেক্ষিত হচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) একথা জানতে পেরে বললেন, “হে আবদুল্লাহ, আমি কি শুনিনি যে, তুমি সারাদিন রোযা রাখো আর সারারাত বন্দেগী করো?” আবদুল্লাহ বলেন, “জী হ্যাঁ, আল্লাহর রাসূল! মহানবী (সা) বললেন, “এরূপ করো না, কয়েকদিন রোযা রাখো আবার কয়েক দিনের জন্যে ছিড়ে দাও, রাতে বন্দেগীও করো আবার ঘুমোতেও যাও। তোমার ওপরে তোমার শরীরের অধিকার আছে, তেমনি তোমার ওপরে তোমার স্ত্রীর দাবী আছে এবং তোমার ওপর তোমার অতিথিরও দাবী আছে......।” (বুখারী)
এ ব্যাপারে প্রখ্যাত সাহাবী সালমান ফারসী এবং তাঁর অন্তরঙ্গ আবু দারদার মধ্যেকার ঘটনাটিও প্রণিধানযোগ্য। রাসূলুল্লাহ (সা) সালমান ও আবু দারদার মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন কায়েম করে দিয়েছিলেন। একদা সালমান আবু দারদার বাড়িতে বেড়াতে গেলেন। দেখলেন আবু দারদার স্ত্রী উমআল দারদা জীর্ণবসন পরিহিতা। তিনি এর কারণ জিজ্ঞেস করলে উমআল দারদা বললেন আপনার ভাই দুনিয়াবী (সাজগোজে) আগ্রহী নন। ইতিমধ্যে আবু দারদা এলেন এবং সালমানের জন্যে খাবারের আয়োজন করলেন। সালমান তার সাথে আবু দারদাকে খেতে বললে তিনি বললেন, ‘আমি রোযা আছি’। তখন সালমান বললেন, ‘তুমি না খেলে আমিও খাব না।’ সুতরাং আবু দারদাও সালমানের সাথে খেলেন। রাতে আবু দারদা নামাযের জন্যে উঠলে সালমান তাকে ঘুমোতে যেতে বললেন। দারদা তাই করলেন। আবু দারদা পুনরায় শয্যাত্যাগ করলে সালমান আবার তাকে ঘুমোতে যেতে বললেন। শেষরাতে সালমান আবু দারদাকে উঠতে বললেন এবং উভয়ে নামায আদায় করলেন। পরে আবু দারদাকে সালমান বললেন, “তোমার ওপরে তোমার প্রভুর অধিকার আছে, তোমার ওপর তোমার আত্মার অধিকার আছে, তোমার ওপর তোমার পরিবারের অধিকার আছে, সুতরাং প্রত্যেককে তার ন্যায্য অধিকার দাও।” আবু দারদা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে এ ঘটনা বিবৃত করলেন। তিনি বললেন: “সালমান সত্য কথাই বলেছে।” (বুখারী ও তিরমিযী)
ধর্মীয় চরমপন্থার ধারণা
ধর্মীয় গোঁড়ামির প্রতিকার করতে হলে সর্বপ্রথমে এর সঠিক সংজ্ঞা, ব্যাখ্যা ও গভীর পর্যালোচনা প্রয়োজন। বিশুদ্ধ ইসলামী চেতনা ও শরীয়ার ভিত্তিতেই বিষয়টির বিচার বিশ্লেষণ করতে হবে। অন্য কোনো মানদন্ডে বিচার করলে তার কোনো মূল্য নেই, কেবল ব্যক্তিগত মতামতের কোন অবকাশ থাকতে পারে না। এ প্রসঙ্গে কুরআন বলছে: “যদি তোমাদের মধ্যে কোন বিষয়ে মতভেদ সৃষ্টি হয় তবে তা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কাছে পেশ করো যদি তোমরা আল্লাহ ও কিয়ামতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে থাকো।” (৪:৫৯)
মুসলিম উম্মাহর সমগ্র ইতিহাসে এ ব্যাপারে ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, মুসলমানদের মধ্যে বিভেদের বিষয় আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কাছে পেশ করার অর্থ হচ্ছে আল্লাহর কিতাব, আল কুরআন এবং মহানবী (সা)-এর সুন্নাহর মধ্যে এর সমাধান অন্বেষণ। শরীয়ভিত্তিক এরুপ অনুমোদন ছাড়া মুসলিম যুব সমাজ-যাদের বিরুদ্ধে চরমপন্থার অভিযোগ আনা হয়েছে-মুসলিম আলিমদের ফতোয়াবাজির প্রতি কর্ণপাত করবে না এবং তাদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ অস্বীকার করে যাবে। অধিকন্তু তারা প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধেই অজ্ঞতা ও মিথ্যাচারের অভিযোগ আনবে।
এখানে উল্লেখ্য, ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইদ্রিস আশ-শাফিঈর বিরুদ্ধে রাফেজী হওয়ার অভিযোগ আনা হয়েছিল। ক্ষুব্ধ হয়ে তিনি কোনো পরোয়া না করে এই সস্তা অভিযোগের বিরোধিতা করে একটি শ্লোক পাঠ করেন যার অর্থ হচ্ছে: “আহালে বায়েতের সকলের প্রতি ভালবাসাই যদি হয় প্রত্যাখ্যান তবে মানুষ ও জিনকে সাক্ষী করে বলছি যে, আমি একজন প্রত্যাখ্যানকারী।” বর্তমান যুগের একজন ইসলাম প্রচারক তার বিরুদ্ধে “প্রতিক্রিয়াশীলতার” অভিযোগ শুনে বলেন “কুরআন ও সুন্নাহর সুনির্দিষ্ট অনুসরনই যদি প্রতিক্রিয়াশীলতা তাহলে আমি প্রতিক্রিয়াশীল হিসেবেই বাঁচতে, মরতে ও পুনরুত্থিত হতে চাই।”
আসলে “প্রতিক্রিয়াশীলতা”, “অনমনীয়তা”,“গোড়ামী” ইত্যাদি শব্দের সঠিক সংজ্ঞা নিরূপণ করা অত্যাবশ্যক। তাহলেএক গ্রুপের বিরুদ্ধে আরেক গ্রুপের এসব শব্দের অপব্যবহার যেমন রোধ করা যাবে তেমনি ডান-বাম বলে পরিচিত বিভিন্ন বুদ্ধিজীবী ও সামাজিক মহল এসব শব্দের সুবিধাবাদী মনগড়া ব্যাখ্যাও দিতে পারবে না। একইভাবে “ধর্মীয় চরমপন্থা” শব্দটির সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা নির্ণীত না হলে সবাই নিজ নিজ মর্জি মাফিক এর প্রয়োগ করবে। ফলত মুসলিম সমাজে বিভেদ ক্রমবিস্তৃত হতে থাকবে আল-কুরআন ঘোষণা করেছে:
“যদি সত্য তাদের ইচ্ছা মাফিক নির্ধারিত হতো তাহলে আকাশ ও পৃথিবী এবং উভয়ের মধ্যস্থিত সব কিছু বিভ্রান্তি ও দুর্নীতি পূর্ণ হয়ে উঠতো।” (২৩:৭১)
এখন আমি দু\'টো গুরুত্বপূর্ন বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করবো। প্রথম, একটি মানুষের সাধুতার (piety) মাত্রা এবং যে পরিবেশের মধ্যে তিনি বাস করেন তা বহুলাংশে অন্য মানুষের প্রতি তার মনোভাব গঠনের প্রভাবিত করে থাকে। কঠোর ধর্মীয় পটভুমি থেকে গড়ে ওঠা একজন মানুষ কারো মধ্যে সমান্যতম বিচ্যুতি বা অবহেলা দেখলে সহ্য করতে পারেন না। তার দৃষ্টিতে বিচার করে তিনি যদি দেখেন যে এমন মুসলমানও আছে যারা তাহাজ্জুদ পড়ে না বা নফল নামায পড়ে না তবে তার বিষ্ময়ের ঘোর কাটতে বেশ সময় লাগবে বৈ কি। এটা ঐতিহাসিকভাবেই খাঁটি কথা। মানুষের আমল ও আখলাকের পরীক্ষা করলে দেখা যাবে, তাবেঈন এবং রাসূলুল্লাহ (সা) ও তাঁর সাহাবীদের নিকটবর্তী যুগের লোকদের আমলের তুলনায় পরবর্তী লোকদের (মুসলমানদের) আমল-আখলাক ততোটা উজ্জ্বল নয়। একটি প্রাবাদে আছে: “পরবর্তী লোকদের নেক কাজ পূর্ববর্তী লোকদের ত্রুটির সমতুল্য।” এখানে আনাস ইবনে মালিক (রা) তার সমসাময়িক তাবেঈনদের উদ্দেশ্যে যা বলতেন তা স্মর্তব্য “আপনারা তুচ্ছ জ্ঞান করে অনেক কাজ করছেন অথচ একই কাজ রাসূলুল্লাহ (সা) -এর আমলে ভয়ানক পাপ বলে গণ্য করা হতো।” একই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করতেন হযরত আয়েশা (রা)। তিনি বিখ্যাত কবি লাবিদ ইবনে রাবিয়ার একটি শ্লোক আবৃত্তি করতেন। তিনি তার এই শ্লোকে এই বলে বিলাপ করেছেন যে, সমাজে অনুকরণীয় সজ্জন ব্যক্তিদের অন্তর্ধানে যে শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে তা স্থান দখল করেছে ছন্নছাড়ারা যাদের সঙ্গ মামড়ি-পড়া পশুদের মতোই বিষাক্ত। হযরত আয়েশা (রা) এই ভাবে বিস্মিত হতেন যে লাবিদ আজ বেঁচে থাকলে বর্তমান সমাজের চেহারা দেখে কী মনে করতেন! হযরত আয়েশা (রা) -এর ভাগ্নে উরওয়াহ ইবনে আল জুবায়েরও এই শ্লোকটি আবৃত্তি করে ভাবতেন আজ হযরত আয়েশা (রা) ও বেঁচে থাকলে এ যুগের অধঃপতনকে কী চোখে দেখতেন! এবার আমরা এর উল্টোটা দেখি। যে ব্যক্তির ইসলাম সম্পর্কে তেমন জ্ঞান বা আনুগত্যবোধ নেই কিংবা সে এমন এক পরিবেশে গড়ে উঠেছে যেখানে শরীয়ত উপেক্ষিত বরং আল্লাহ যা নিষেধ করেছেন তাই করা হয় নিদ্বির্ধায়, সেই ব্যক্তি ইসলামের প্রতি কারো সামান্য অনুরাগ দেখলেই তাকে গোঁড়া বা চরমপন্থী বলে মনে করবে। এমন ব্যক্তি সাধুতার ভান করতে অভ্যস্ত এবং সে ধর্মের কোনো কোনো বিষয়ের সমালোচনা করেই ক্ষান্ত হবে না, এরা যৌক্তিকতাকেও অস্বীকার করে বসবে। ইসলামের প্রতি যারা অনুরক্ত তাদেরকে সে অভিযুক্ত করবে এবং কোনটা হারাম আর কোনটা হলাল সে বিষয়ে তর্ক করতে তার জুড়ি মেলা ভার। অবশ্য ইসলাম থেকে দুরত্বে অবস্থানের দরুনই এসব মানুষের এরুপ দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে। ভিন্ন আদর্শ ও জীবন ধারার প্রভাবের কারণে কোনো কোনো মুসলমানের কাছে পানাহার, সৌন্দর্যবোধ, শরীয়তের পাবন্দীর তাগিদ এবং ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্টার মতো সুষ্পষ্ট ইসলামী মূল্যবোধগুলো ধর্মীয় গোঁড়ামী বা চরমপন্থা ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না। এমন ব্যক্তির চোখে শ্বশ্রুমন্ডিত মুসলমান তরুণ কিংবা হিজাব পরা মুসলিম তরুণী মাত্রই চরমপন্থী। এমনকি ভাল কাজের আদেশ ও খারাপ কাজের নিষেধকে গোঁড়ামী এবং ব্যক্তি স্বাধীনতার হস্তক্ষেপ বলে মনে করা হয়। আমরা জানি আমাদের ধর্ম বিশ্বাসের মূল ভিত্তি হচ্ছে একমাত্র ইসলামকেই সত্য বলে মেনে নেয়া এবং যারা এটা বিশ্বাস করে না তারা বিভ্রান্ত বলে স্বীকার করা। কিন্তু এ সমাজে এমন মুসলমানও দেখা যায় যারা এটা মানতে নারাজ। যারা ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্মগ্রহণ করেছে তাদের কাফির গণ্য করতে তাদের ঘোরতর আপত্তি! এটাকেও তারা উগ্রতা ও গোঁড়ামী বলে মনে করে। আর এটা এমন একটা ইস্যু, যে ব্যাপারে আমরা কখনোই আপোস করতে পারি না।
দ্বিতীয়ত, কেউ জোরালো মতামত অবলম্বন করলেই তাকে “ধর্মীয় চরমপন্থী” বলে অভিযুক্ত করা অন্যায়। কেউ যদি তার মতামত সম্পর্কে স্থির নিশ্চিত হয় যে, এ ব্যাপারে শরীয়তেরও অনুমোদন রয়েছে তবে সে তার মত অনুযায়ী স্বাচ্ছন্দে চলতে পারে। তার পেছনে ফুকাহাদের সমর্থন দুর্বল বলে অন্যেরা মনে করলেও তাতে কিছু আসে যায় না। সে তো কেবল তার চিন্তা ও বিশ্বাসের জন্যে দায়ী। সে যদি ধর্মীয় বাধ্যবাধকতাকে সীমিত গন্ডিতে অনুশীলন না করে নিজের ওপর অতিরিক্ত বোঝা চাপিয়ে নেয়, কারো বলার কিছু নেই। কেননা সে হয়তো মনে করে অতিরিক্ত আমলের মাধ্যমে আল্লাহর রেজামন্দী হাসিল করা সহজ হবে। বস্তুত এসব বিষয়ে মত পার্থক্যের অবকাশ আছে। কেউ একটা বিষয়কে সহজভাবে নেয় আবার অনেকে এর বিপরীত আচরণে অভ্যস্ত। রাসূলে কারীম (সা) -এর সাহাবীদের বেলায়ও একথা সত্য। উদাহরণস্বরুপ, ইবনে আব্বাস (রা) ধর্মীয় বিষয়গুলোর প্রতি সহজতর দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করতেন, কিন্তু ইবনে উমর (রা) ছিলেন কঠোর মনোভাবাপন্ন। এই প্রেক্ষাপটে, একজন মুসলমানের পক্ষে যথেষ্ট হবে যদি সে কোনো একটি মাযহাবের অনুসরণ করে অথবা কুরআন ও সুন্নাহভিত্তিক নির্ভরযোগ্য ইজতিহাদের পন্থা অনুসরণ করে। অতএব যদি কেউ চার ইমাম যথা শাফিঈ, আবু হানিফা, মালিক ও আহমদ ইবনে হাম্বলের (রা) মাযহাবের মধ্যে কোনো একটি অনুসরণ করে এবং তা যদি অন্য কিছু পন্ডিতের বিবেচনায় সমকালীন মতের বিরোধী হয় তাহলেই কি ঐ ব্যক্তিকে চরমপন্থী বা গোঁড়া বলে অভিহিত করা সঙ্গত হবে? আমাদের কি কোনো অধিকার আছে অন্য কোনো ব্যক্তির ইজতিহাদী পন্থা বেছে নেয়ার অধিকারকে খর্ব করার?
বহু ফকীহ এই রায় দিয়েছেন যে, মুখমন্ডল ও হাত বাদ দিয়ে মুসলিম মহিলারা সমগ্র দেহকে আবৃত করে- এমন পোষাক পরতে পারে। হাত ও মুখমন্ডলকে ছাড় দেয়ার পক্ষে তারা কুরানের এই আয়াতকে প্রমাণ হিসেবে পেশ করেন: “..... তাদের সৌন্দর্য ও অলঙ্কার প্রদর্শন করা উচিত নয়, তা ব্যতীত যা (অবশ্যই সাধারণভাবে) দৃষ্টিগোচর হয়।” (২৪:৩১)
এর পক্ষে তারা হাদীসের প্রামাণ্য ঘটনা এবং ঐতিহ্যের সমর্থনও পেশ করেছেন। বহু সমকালীন আলেমও এই মতের সমর্থক, আমি নিজেও।পক্ষান্তরে, অনেক আলেম যুক্তি পেশ করে বলেছেন যে, হাত এবং মুখও ‘আওরা’ অর্থাৎ অবশ্যই ঢাকতে হবে। তারাও কুরআন, আল-হাদীস ও প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্য থেকে প্রমাণ পেশ করেন। সমসাময়িক বহু আলেম এই মতের সমর্থক। এদের মধ্যে পকিস্তান, ভারত, সউদী আরব ও উপসাগরীয় দেশের আলেমও রয়েছেন। তারা মুসলিম মহিলাদের মুখ ঢাকতে এবং হাত মোজা পরতে বলেন। এখন কোনো মহিলা যদি ঈমানের অঙ্গ হিসেবে এটা পালন করেন তবে তাকে কি গোঁড়া বলে চিহ্নিত করতে হবে? কিংবা কোনো ব্যক্তি যদি তার স্ত্রী কন্যাকে এটা মেনে চলার জন্য তাগিদ দেন তাহলে তাকেও কি চরমপন্থী বলে অভিহিত করতে হবে? আল্লাহর বিধান বলে কেউ যা মনে করে তা ছেড়ে দিতে কাউকে বাধ্য করার অধিকার কি আমাদের আছে? তা যদি করি তাহলে কি আমরা আমাদের খেয়ালখুশী চাপিয়ে দেয়া কিংবা চরমপন্থী বরে অভিযোগ এড়ানোর জন্যে আরেকজনকে আল্লাহর ক্রোধের দিকে ঠেলে দেয়ার অযাচিত নছিহত করব না? নাচ-গান, ছবি ও আলোকচিত্রের ব্যাপারে যারা কঠোর মনোভাব পোষণ করেন সে ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। এসব কঠোর মত আমার ব্যক্তিগত ইজতিহাদ থেকে শুধু নয় বরং অন্যান্য প্রখ্যাত আলেমদের ইজতিহাদ থেকেও ভিন্নতর। কিন্তু স্বীকার করতেই হয় যে এসব মতামতের সাথে প্রাথমিক যুগ ও সমসাময়িক অনেক আলিমদের দৃষ্টিভঙ্গির সাজুয্য রয়েছে।
আমরা অনেকে শার্ট ও প্যান্টের পরিবর্তে ছওব (ঢিলা জামা-কাপড়) পরা অথবা মেয়েদের সাথে মোসাফাহা না করাকে গোঁড়ামি বলে সমালোচনা করি; কিন্তু খোদ উসূলে ফিকাহ এবং উম্মাহর ঐতিহ্যের মধ্যেই এসব বিষয়ে বিতর্কের বীজ নিহিত রয়েছে। মতপার্থক্য থাকার সুযোগের কারণেই সমসাময়িক আলিমরা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মত প্রকাশ করেন এবং জোর প্রচার চালান। ফলত, আল্লাহর রহমতের আশা এবং তাঁর শাস্তির ভয়ে কিছু নিষ্ঠাবান মুসলিম তরুণ এসব বিষয় মেনে নেন। সুতরাং ফকীহর রায়ের ভিত্তিতে আল্লাহর সন্তষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে কেউ যদি ধর্মচর্চায় কঠোরতা অবলম্বন করে তবে সে জন্যে তাকে নিন্দা করা বা গোঁড়ামির অপবাদ দেয়া সমীচীন নয়। তার বিশ্বাসের পরিপন্থী আচরণে তাকে বাধ্য করার অধিকার আমাদের নেই। আমাদের একমাত্র কর্তব্য হচ্ছে প্রজ্ঞা, যুক্তি ও ধৈর্যের মাধ্যমে এমনভাবে তাকে বোঝানোর চেষ্টা করা যাতে আমরা যেটাকে সত্য বলে বিশ্বাস করি তা গ্রহণে সে উদ্বুদ্ধ হয়।
চরমপন্থার লক্ষণ
চরমপন্থার প্রথম লক্ষণ হচ্ছে অন্ধতা। চরমপন্থী বা গোঁড়া ব্যক্তি নিজের মতের প্রতি একগুঁয়ে ও অসহিষ্ণুর মতো এমন অটল থাকে যে, কোনো যুক্তিই তাকে টলাতে পারে না। অন্য মানুষের স্বার্থ, আইনের উদ্দেশ্য ও যুগের অবস্থা সম্পর্কে তার স্বচ্ছ ধারণা থাকে না। তারা অন্যের সাথে আলোচনায়ও রাজী হয় না যাতে তাদের মতামত অন্যের মতামতের সাথে তুলনামূলক পর্যালোচনা করা যায়। তাদের বিবেচনায় যা ভাল হয় কেবল তা অনুসরণেই তারা প্রবৃত্ত হয়। যারা অন্যের মতামত দাবিয়ে রাখা ও উপেক্ষা করার চেষ্টা চালায় এবং যারা এর জন্য তাদেরকে অভিযুক্ত করে, আমরা উভয়কেই সমভাবে নিন্দা করি। বস্তুতপক্ষে যারা নিজেদের মতকেই কেবল নির্ভেজাল বিশুদ্ধ এবং অন্যদেরকে ভ্রান্ত বলে মনে করে তাদেরকে কঠোরভাবে নিন্দা করা ছাড়া গত্যন্তর নেই বিশেষ করে তখন, যখন তারা কেবল ভিন্নমতের জন্যে প্রতিপক্ষকে জাহিল, স্বার্থন্বেষী, অবাধ্য তথা ফিসকের অভিযোগে অভিযুক্ত করে। তাদের আচরণে মনে হবে যেন তারাই নির্ভেজাল, খাঁটি বিশুদ্ধ এবং তাদের প্রতিটি কথাই যেন ওহী বা এলহাম! এ ধরণের একগুঁয়ে দৃষ্টিভঙ্গি উম্মাহর ইজমার পরিপন্থী। কেবলমাত্র কুরআন ও সুন্নাহ ছাড়া অন্য যে কোনো ব্যক্তির যে কোনো মত গ্রহণ বা বর্জন করা যেতে পারে। এটাই উম্মাহর সর্ববাদী সম্মত রায়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় কিছু লোক বিভিন্ন জটিল বিষয়ে নিজেদের ইজতিহাদের অধিকার প্রয়োগ করে খেয়ালখুশী মতো রায় দিয়ে থাকেন। কিন্তু সমকালীন বিশেষজ্ঞ আলিমদেরকে একক বা যৌথভাবে ইজতিহাদের অধিকার প্রয়োগ করতে দেখলে তারা বেজায় নাখোশ হন। অথচ ঐ সব ব্যক্তি কুরআন ও সুন্নাহর এমন হাস্যকর ব্যাখ্যা দেন যা আমাদের পূর্বপুরুষ বুজুর্গানে দ্বীন এবং সমসাময়িক আলিমদের রায় বা সিদ্ধান্তের পরিপন্থী। মজার ব্যাপার হচ্ছে, তারা নিজেদেরকে হযরত আবু বকর, উমর, আলী ও ইবনে আব্বাসের (রা) সমপর্যায়ের মনে করেন। তাদের এই উদ্ভট দাবীতে তেমন ক্ষতি ছিল না যদি তারা তাদেরকে কেবল সমসাময়িক পন্ডিতদের সমপর্যায়ের মনে করতেন।
সুতরাং নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে, চরমপন্থা বা গোঁড়ামির পরিস্কার লক্ষণ হচ্ছে অন্ধতা। তার দাবীর সারকথা: “বলার অধিকার কেবল আমার, তুমি কেবল শুনবে। আমি পথ দেখাবো, তুমি সেই পথে চলবে। আমার মত অভ্রান্ত, তুমি ভ্রান্ত। আমার ভুল হতে পারে না, আর তোমারটা কখনো ঠিক হতেই পারে না।” অর্থাৎ একজন তার অন্ধমতানুযায়ী কোনোভাবে অন্যের সাথে সমঝোতায় আসতে পারে না। অথচ আমরা জানি, সমঝোতা ছাড়া সমাজ সংহত হতে পারে না। সমঝোতা কেবল তখনই সম্ভব যখন কেউ মধ্যপন্থায় অবস্থান নেয়। কিন্তু একজন চরমপন্থী মধ্যপন্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, বিশ্বাস তো দূরের কথা। জনগণের সংগে তার সম্পর্ক পূর্ব ও পশ্চিমের সম্পর্কের মতো- যতই তুমি একটির নিকটে যাবে তুমি অন্যটি হতে দূরে সরে যাবে। বিষয়টি আরো জটিল হয়ে যায় যখন এ রকম ব্যক্তি অন্যকে বাধ্য করার মনোভাব গ্রহণ করে কেবল শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে, অনেক সময় অভিযোগের মাধ্যমে যে প্রতিপক্ষ অবিশ্বাসী, বিপথগামী কিংবা বেদাতী। এরূপ বুদ্ধিবৃত্তিক সন্ত্রাস শারীরিক সন্ত্রাসের চেয়েও ভয়ঙ্কর।
চরমপন্থার দ্বিতীয় পরিচয় হচ্ছে, সর্বক্ষণ বাড়াবাড়ি করার নীতিতে অটল থাকা এবং সমঝোতার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকা সত্ত্বেও অন্যকে তার মতো আচরণে বাধ্য করতে প্রয়াসী হওয়া যদিও তার কাজটি আল্লাহর বিধানসম্মত নয়। তাকওয়া ও সতর্কতার কারণেও এক ব্যক্তি ইচ্ছা করলে কোনো কোনো বিষয়ে কখনো কখনো কঠোর মত পোষণ করতে পারে। কিন্তু এটা এমন অভ্যাসে পরিণত হওয়া উচিত নয় যাতে সে যেখানে প্রয়োজন এমন ক্ষেত্রেও সহজ সরল বিষয়গুলো পরিহার করে। এরুপ দৃষ্টিভঙ্গি কুরআন ও হাদীসের শিক্ষার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। আল্লাহ বলেন: “আল্লাহ তোমাদের জন্যে যা সহজ তা চান, যা তোমাদের জন্যে ক্লেশকর তা চান না।” (২:১৮৫)
আল্লাহ রাসূলও (সা.) ইতিপূর্বে উদ্ধৃত হাদীসে বলেছেন: “(ধর্মীয় বিষয়গুলো) সহজ করে তুলে ধরো কঠিন করো না।” (সকল প্রামাণ্য সূত্রে সমর্থিত)
তিনি আরো বলেছেন : “তাঁর প্রদত্ত সুবিধা ভোগ করলে আল্লাহ খুশী হন যেমন (লোকেরা) তাঁর অবাধ্য হলে তিনি নারাজ হন।” (আহমাদ, বায়হাকী ও তাবারী) এছাড়া রেওয়ায়েত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) কে যখনি দু’টি কাজের মধ্যে একটি বেছে নিতে বলা হয়েছে, গর্হিত না হলে তিনি সহজতম পথটিই সর্বদা বেছে নিয়েছেন।” (বুখারী ও তিরমিযী)
মানুষের জন্যে কোনো কাজকে জটিল করে তোলা কিংবা তার ওপরে চাপ সৃষ্টি করা রাসূলুল্লাহ (সা) -এর উজ্জ্বলতম গুণাবলীর পরিপন্থী। এটি পূর্ববর্তী বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ এবং পরবর্তীকালে কুরআনুল কারীমেও উল্লেখ করা হয়েছে: “যিনি তাদের জন্যে পবিত্র বস্তু বৈধ ও উত্তম (পবিত্র) এবং অপবিত্র বস্তু অবৈধ করেন এবং মুক্ত করেন তাদেরকে তাদের গুরুভার হতে ও শৃংখল হতে যা তাদের ওপর ছিল।” (৭:১৫৭)
এ কারণে রাসূলুল্লাহ (সা) কেবল একাকী নামযকে দীর্ঘ করতেন। আসলে তিনি পা ফুলে না ওঠা পর্যন্ত সারা রাত ধরে নামায পড়তেন। কিন্তু যখন তিনি জামায়াতে ইমামতি করতেন তখন তাঁর অনুসারীদের সহ্য ক্ষমতা ও পরিস্থিতির বিচারে নামায সংক্ষিপ্ত করতেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, “যখন তোমাদের মধ্যে কেউ নামাযের ইমামতি করে তখন তা সংক্ষিপ্ত করা উচিত, কেননা সেখানে দুর্বল, রুগ্ন ও বৃদ্ধলোক থাকে; কিন্তু কেউ একাকী নামায পড়লে ইচ্ছা মতো দীর্ঘ করতে পারো।” (বুখারী)
আবু মাসুদ আল আনসারী বর্ণনা করেছেন যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলল, “হে আল্লাহর রাসূল, আমি সালাতুল ফজরে হাযির হই না, কেননা অমুক অমুক নামাযকে দীর্ঘ করে থাকে। ” রাসূলুল্লাহ (সা) অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, “হে মানুষেরা তোমরা মানুষকে উত্তম কাজের (নামায) প্রতি বিতৃষ্ণ করতে চাও? যখন কেউ নামায পড়াবে তখন তা সংক্ষিপ্ত করবে, কেননা সেখানে দুর্বল, বৃদ্ধ ও ব্যস্ত লোক থকে। ” আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, রাসূলুল্লাহ (সা) একইভাবে রাগন্বিত হয়েছিলেন যখন জানতে পারেন যে, মুয়ায (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন: “যখন আমি নামাযের জন্যে দাঁড়াই তখন আমি একে দীর্ঘ করার ইচ্ছা করি, কিন্তু শিশুর কান্না শুনে আমি নামায সংক্ষিপ্ত করি, কারণ আমি মাতাদের কষ্টে ফেলতে চাই না।”
অবশ্য করণীয় কাজগুলোর মতো ঐচ্ছিক কাজগুলো সম্পন্ন করার চাপ দেয়াটাও বাড়াবাড়ির শামিল। অনেক সময় মাকরুহাতের জন্যে এমনভাবে কৈফিয়ত তলব করা হয় যেন এগুলো মুহাররামাতের (হারাম সমূহের) অন্তর্ভূক্ত। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ যেসব কর্তব্য কর্মের সুষ্পষ্ট আদেশ দিয়েছেন কেবল সেসব ব্যাপারেই কৈফিয়ত তলব করা যায়। এর বাইরে অতিরিক্ত সকল ধরনের ইবাদতই ঐচ্ছিক। নিম্নোক্ত ঘটনাটি থেকে বোঝা যাবে এটাই রাসূলুল্লাহ্ (সা) -এর মত: একদা এক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ (সা) কে অবশ্য পালনীয় কাজ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি মাত্র তিনটি কাজের কথা উল্লেখ করলেন- নামায, যাকাত ও রোযা। এছাড়া আর কিছু করার আছে কিনা জিজ্ঞাসিত হয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা) না-বাচক জবাব দিলেন এবং বললেন যে, বেদুঈন ইচ্ছে করলে বেশী কিছুও করতে পারে। বেদুঈন বিদায় নেয়ার আগে প্রতিজ্ঞা করলো, রাসূলুল্লাহ (সা) যা কিছু বলেছেন তার চেয়ে বেশীও করবে না, কমও করবে না। মহানবী (সা) একথা শুনে বললেন, “যদি সে সত্য কথা বলে থাকে তবে সে সফল হবে, অথবা বলেছিলেন “তাকে জান্নাত মঞ্জুর করা হবে।” (বুখারী)
আজকের যুগে একজন মুসলমান যদি অবশ্য কর্তব্য কাজগুলো সম্পন্ন করে এবং মুহাররামাতের সবচেয়ে জঘন্য কাজ থেকে দূরে থাকে তবে তাকে ইসলামের অন্তর্ভূক্ত বলে গণ্য করা যায় যতক্ষণ পর্যন্ত সে আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি আনুগত্য বজায় রাখে। এমনকি যদি সে ছোটখাটো মুহাররামাতের কাজ করে ফেলে তবে দৈনিক পাঁচ ওয়াক্তের নামায, জুমা’র নামায ও রোযার বদৌলতে তার ছোট অন্যায়গুলোর কাফফারাহ হয়ে যাবে। কেননা কুরআন ঘোষণা করছে: “ভাল কাজ খারাপ কাজকে অবশ্যই মিটিয়ে দেয়।” (১১:১১৪)
আরেকটি আয়াতে আছে: “যদি তোমরা সবচেয়ে জঘন্য নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকো তবে আমরা তোমাদের সকল খারাপ কাজকে মুছে ফেলবো এবং তোমাদেরকে উচ্চ সম্মানের স্থানে আসীন করবো।” (৪:৩১)
একজন মুসলমান যদি কিছু বিতর্কমূলক বিষয় অনুসরণ করেন যার হালাল বা হারাম হওয়া সম্পর্কে আমরা নিশ্চিত নই অথবা এমন কিছু কাজ পরিত্যাগ করেন যার ওয়াজিব হওয়া বা মুবাহ হওয়া অনিশ্চিত, তাহলে কুরআন ও সুন্নাহর উপরিউক্ত প্রমাণের প্রেক্ষিতে তাকে কি আমরা ইসলাম বহির্ভূত বলে ঘোষণা করতে পারি: আর এ কারণেই আমি কিছু সাধু লোকের কঠোর মতের বিরোধী। তারা শুধু নিজেদের আচরণের মধ্যেই এই গোঁড়ামি সীমাবদ্ধ রাখেন না, অন্যকেও এতে অহেতুক প্রভাবিত করতে চান। আরো আপত্তি আছে। এসব লোক কোনো কোনো আলিমের বিরুদ্ধেও বিশেদগার করতে কুন্ঠিত হন না। অথচ এসব আলিম সত্যিকার অর্থে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে সাধারণ মানুষের ওপর অনর্থক চাপিয়ে দেয়া বিধি-নিষেধের বোঝা হালকা করতে চান।
চরমপন্থার আরেকটি লক্ষন হচ্ছে নির্দয় কঠোরতা। চরমপন্থীদের স্থানকালের বিবেচনা জ্ঞান নেই। নও-মুসলিমদের প্রতি অন্তত প্রাথমিক অবস্থায় নম্র আচরণ করা উচিত-সেই নও-মুসলিম মুসলিম অথবা অমুসলিম যে দেশেরই হোক। এমনকি ধর্মের প্রতি সদ্য অনুরক্ত মুসলমানদের প্রতিও সহৃদয় দৃষ্টি দেয়া দরকার। নব দীক্ষিত মুসলমানদের প্রথমেই ছোটখাট বিষয়গুলো মানতে বাধ্য করানো উচিত নয়। প্রথমে তাদেরকে মৌলিক বিষয়গুলো বোঝার সুযোগ দিতে হবে। তাদের ধ্যান-ধারণা, চিন্তাধারা ইসলামের আলোকে সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে। একবার তাদের মনে ঈমানের চেতনা বদ্ধমূল হয়ে গেলেই ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভ এবং ক্রমান্বয়ে বাস্তব জীবনে আল্লাহর বিধি বিধান রূপায়ণের তাগিদ সৃষ্টি করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জীবন থেকে আমরা এর সত্যতা খুঁজে পাই। হযরত মুয়ায (রা) কে ইয়ামেনে পাঠানোর সময় হযরত মুহাম্মদ (সা) বলেছিলেন, “তুমি আহলে কিতাবের একটি জনগোষ্ঠীর কাছে যাচ্ছ। সেখানে পৌঁছে তাদেরকে এই সাক্ষ্য দিতে বলবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মা’বুদ নেই। এবং হযরত মুহাম্মদ (সা) তাঁর প্রেরিত রাসূল। যদি তারা এটা মেনে নেয় তখন তাদেরকে বলবে যে, আল্লাহ দিনে রাতে পাঁচ বার নামায আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন। তারপর বলবে যে, আল্লাহ তোমাদের মধ্যে ধনীদের কাছ থেকে যাকাত আদায় করে গরীবদের মধ্যে বন্টনের আদেশ দিয়েছেন। ........ (সকল প্রামাণ্য সূত্রে সমর্থিত)
মুয়ায (রা)- এর প্রতি রাসুলুল্লাহ (সা)-এর উপদেশের মধ্যে দাওয়াতী কাজের ক্রমিক পদ্ধতি লক্ষণীয়। উত্তর আমেরিকা সফরের সময় আমি কিছু নিষ্ঠাবান মুসলিম তরুণের আচরণে ক্ষুব্ধ হয়েছিলাম। এই তরুণরা একটি মুসলিম গ্রুপের সাথে সংশ্লিষ্ট। সেখানে মুসলমানরা সাধারণত শনি ও রবিবারের ভাষণের সময় চেয়ারে বসতো। ঐ তরুণরা মনে করে মাদুরে কেবলামুখী হয়ে বসা উচিত। এছাড়া শার্ট প্যান্টের পরিবর্তে ঢিলেঢালা পোষাক পরিধান এবং ডাইনিং টেবিলের পরিবর্তে মেঝেতে বসে খাওয়া উচিত। বিষয়টির ওপর তরুণেরা বিতর্কের ঝড় তুলেছিলো। উত্তর আমেরিকার মতো জায়গায় এরূপ দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণ দেখে আমি ক্ষুব্ধ না হয়ে পারিনি। সুতরাং আমি আমার ভাষণে বললাম : এই বস্তুবাদী সমাজে আপনাদের প্রধান কাজে হওয়া উচিত তাওতীদ ও আল্লাহর বন্দেগীর দিকে মানুষকে আহবান করা এবং পরকাল ও মহান ইসলামী মূল্যবোধের প্রতি তাদের আগ্রহ সৃষ্টি করা। সেই সাথে বৈষয়িক উন্নতির শীর্ষে আরোহণ করেও এই দেশগুলো যে জঘন্য ক্রিয়াকলাপে নিমজ্জিত তার পরিণতি সম্পর্কেও তাদের হুঁশিয়ার করে দিতে হবে। ধর্মীয় আচার-আচরণ ও খুঁটিনাটি বিষয়ে পদ্ধতিগত উৎকর্ষ অর্জনের বিষয়টি স্থান ও কালের প্রেক্ষাপটে বিচার করা উচিত। এর আগে আমাদের নিশ্চিত করতে হবে যে, ধর্মের মৌলিক ও অত্যাবশ্যক নীতিমালা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
আরেকটি ইসলামী কেন্দ্রের ঘটনা উল্লেখ করছি। মসজিদে ঐতিহাসিক ও শিক্ষামূলক চলচ্চিত্র প্রদর্শনী নিয়ে সেখানে বেশ হৈ চৈ হচ্ছিল। প্রদর্শনীর বিরোধীরা অভিযোগ করছেন যে, মসজিদকে সিনেমা হলে পরিণত করা হয়েছে। কিন্তু তারা একথা বেমালুম ভুলে বসেছেন যে, মসজিদের উদ্দেশ্য হচ্ছে মুসলমানদের আধ্যাত্মিক ও জাগতিক উভয় ক্ষেত্রের কর্মকান্ডের কেন্দ্রস্থল হিসেবে এক ব্যবহার করা। হযরত মুহাম্মদ (সা) -এর আমলে মসজিদ ছিলো একাধারে দাওয়া, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক কার্যক্রমের সদর দফতর। এটা সম্ভবত সকলেরই জানার কথা, আবিসিনিয়া থেকে আগত একদল লোককে রাসূলুল্লাহ (সা) মসজিদের মধ্যস্থলে বশা দিয়ে ক্রিয়া প্রদর্শনের অনুমতি দিয়েছিলেন এবং হযরত আয়েশা (রা) তা দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন। (বুখারী এবং অন্যান্য)
গোঁড়ামির চতুর্থ লক্ষণ হচ্ছে, মানুষের প্রতি আচার-আচরণে অশিষ্টতা, উপস্থাপনায় স্থুলতা এবং দাওয়াতী কাজে গোবেচারা ভাব। এসবই হচ্ছে কুরআন ও সুন্নাহর শিক্ষার সাথে সঙ্গতিহীন। আল্লাহ তায়ালা কুশলী ও মধুর ভাষায় ইসলামের প্রতি মানুষকে আহবান করার আদেশ দিয়েছেন: “হিকমতের সাথে ও সদুপদেশ দ্বারা তোমার প্রভুর দিকে (মানুষকে) আহবান জানাও এবং সদ্ভাবে (উৎকৃষ্টতম ও সুবিবেচনা প্রসূত পন্থায়) তাদের সাথে আলোচনা করো।”(১৬:১২৫)
রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রসঙ্গ টেনে কুরআন বলছে: “এখন তোমাদের কাছে তোমাদের মধ্য থেকে একজন রাসূল এসেছেন। তোমাদেরকে যা বিপন্ন করে তা তার জন্যে বেদনাদায়ক, তিনি তোমাদের মঙ্গলকামী, ঈমানদারদের প্রতি তিনি দয়াময় ও করুণাশীল।” (৯:১২৮।
আল কুরআনুল কারীমে সাহাবীদের সাথে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সম্পর্কের রূপ বর্ণনা করে বলা হয়েছে: “আল্লাহর রহমতে আপনি তাদের প্রতি কোমল হৃদয় হয়েছিলেন, আপনি যদি কর্কশ ও কঠোর হৃদয়ের হতেন তাহলে তারা আপনার কাছ থেকে সরে পড়তো।” (৩:১৫৯)
আল কুরআনে মাত্র দুটি ক্ষেত্রে দৃঢ়তা ও কঠোরতার উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমত, যুদ্ধেক্ষেত্রে। যুদ্ধ বিজয় অর্জনের লক্ষ্য দৃঢ়তা ও কঠোরতার অত্যাবশ্যক। এক্ষেত্রে প্রয়োজনে কোমলতা পরিহার করতে হবে অন্তত যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত। কুরআন বলছে, “সেসব অবিশ্বাসীর বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাও, তারা তোমাদের মধ্যে কঠোরতা দেখুক।” (৯:১২৩)
দ্বিতীয়ত, শরীয়তের বিধান অনুযায়ী অপরাধীর শাস্তি কার্যকর করার ব্যাপারে। সেক্ষেত্রে আল্লাহর আইন প্রয়োগের বেলায় নমনীয়তার কোনো অবকাশ নেই। কুরআনের ভাষায়: “ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণী তাদের প্রত্যেককে এক শত বেত মারো। আল্লাহর বিধান কার্যকর করতে তাদের প্রতি দয়া যেন তোমাদেরকে প্রভাবাম্বিত না করে, যদি তোমরা আল্লাহ ও কিয়ামতে বিশ্বাসী হও। ” (২৪:২)
কিন্তু দাওয়াতী কাজের ব্যাপারে সহিংসতা ও কঠোরতার কোনো অবকাশ নেই। এই হাদীসে তার প্রমাণ পাওয়া যায়: “আল্লাহ সকল ব্যাপারে দয়া পছন্দ করেন এবং দয়া সবকিছু সুন্দর করে, সহিংসতা সবকিছু ত্রুটিপূর্ণ করে।” এছাড়া আমাদের বুজর্গ পূর্বপুরুষরাও একথা বলেছেন, “যারা ভাল কাজের আদেশ দিতে চায় তারা যেন তা নম্রতার সাথে করে। ” সহিংসতা আল্লাহর পথে দাওয়াতী কাজের উদ্দেশ্যকেই পন্ড করে দেয়। দাওয়াতী কাজের লক্ষ্য হচ্ছে মানুষের হৃদয় কন্দরে আলোর রশ্মিপাত করা, যে আলোর পরশে তার ধ্যান-ধারণা, চিন্তাধারা, আবেগ-আচরণ রূপান্তরিত হয়ে তাকে একটা নতুন সত্তা হিসেবে সৃজন করবে। সে আল্লাহ্ দ্রোহী থেকে পরিণত হবে একজন আল্লাহ ভিরু ব্যক্তিত্বে। দাওয়াতী কাজ একইভাবে সমাজের প্রচলিত বিশ্বাস, ঐতিহ্য ও পদ্ধতির ভিত্তিমূলে নাড়া দিয়ে তাকে নতুনরূপে গড়তে চায়।
এসব মহান উদ্দেশ্য অর্জন করতে হলে প্রজ্ঞা ও সহৃদয়তা অত্যাবশ্যক। তদুপরি প্রয়োজনে মানুষের প্রকৃতির দিকে লক্ষ্য রাখা। মানব প্রকৃতিতে একগুঁয়েমি, পরিবর্তন বিরোধিতা ও তর্কপ্রিয়তা অন্তর্নিহিত। দাওয়াতী কাজের সময় এই প্রকৃতির মোকাবিলা করার একমাত্র হাতিয়ার হচ্ছে নম্র, কোমল ও কৌশলময় আচরণ। এই হাতিয়ার ব্যবহার করেই উদ্দিষ্ট ব্যক্তির হৃদয়ের মণিকোঠায় স্থান করে নিতে হবে।ফলত তার প্রকৃতি যতোই অনমনীয় হোক এক সময় তাকে নমনীয় হতেই হবে। তার অহঙ্কার-অহমিকা অমায়িকতায় রূপান্তরিত হবেই। আলকুরআন আমাদেরকে এই প্রক্রিয়া অবলম্বেনের দিকেই নজর দিতে বলেছে। এছাড়া পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণ ও তাঁদের উম্মতরা একই প্রক্রিয়ায় দাওয়াতী কাজ চালিয়েছেন। হযরত ইবরাহীম (আ) তাঁর পিতা ও জনগণের প্রতি, শুয়াইব(আ) তাঁর জনগোষ্ঠীর প্রতি, হযরত মূসা (আ) ফেরাউনের প্রতি তথা সূরা ইয়াসিনে (৩৬:২০) উল্লিখিত সাধারণ মানুষের প্রতি ঈমানদারদের দাওয়াতী কাজ একই পন্থায় সম্পন্ন হয়েছে। আর সব দাওয়াতী কাজের মূল কথা ছিলো একটি: তোমরা আল্লাহর বন্দেগী কবুল করো। একজন ঈমানদার যখন তার সমগোত্রীয়দের আল্লাহর পথে দাওয়াত দেন তখন তার মধ্যে সমমর্মিতার আকুল আবেগ প্রতিধ্বনিত হয়। ফেরাউনের প্রতি একজন ঈমানদারের দাওয়াতের মধ্যেও সেই ব্যঞ্জনা ফুটে উঠেছে: “হে আমার স্বজাতি! আজ তোমাদেরই কর্তৃত্ব, দেশে তোমরাই প্রবল; কিন্তু আল্লাহর আযাব যখন আমাদের ওপর আপতিত হবে তখন আমাদেরকে কে সাহায্য করবে? (৪০:২৯)
অতঃপর তিনি আল্লাহর বাণীর প্রতি কর্ণপাত না করার পরিণামে অতীতের জাতিসমূহকে কিভাবে আযাব ভোগ করতে হয়েছে তা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন: “হে আমার স্বজাতি! আমি তোমাদের জন্যে পূর্ববর্তী সম্প্রদায়সমূহের শাস্তির দিনের অনুরুপ দুর্দিনের আশঙ্কা করি যেমন ঘটেছিলো নূহ, আদ, সামূদ ও তাদের পূর্ববর্তীদের ক্ষেত্রে। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের ওপর কোন অবিচার করতে চান না।” (৪০: ৩০-৩১)
এর পর তিনি কেয়ামত দিবসের ভয়াবহতা সম্পর্কে বর্ণনা দিয়ে বলছেন--
“হে আমার স্বজাতি! আমি তোমাদের জন্যে সেই কিয়ামত দিবসের ভয় করছি যেদিন তোমরা পরস্পরকে ডাকবে (এবং বিলাপ করবে); কিন্তু সেদিন তোমরা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পালাতে থাকবে। আল্লাহর তরফ থেকে সেদিন তোমাদেরকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না। আল্লাহ যাকে বিভ্রান্ত করেন তার জন্যে কোন পথপ্রদর্শক নেই।” (৪০:৩২-৩৩)
এভাবে আমরা দেখি একজন নবী মিনতি সহকারে নম্র ও কোমল ভাষায় দাওয়াত দিয়ে চলেছেন যার মধ্যে হুঁশিয়ারি আছে, আশার প্রেরণাও আছে:
“হে আমার কওম! আমাকে অনুসরণ করো। আমি তোমাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করবো। ইহকালীন জীবন (অস্থায়ী) উপভোগের বস্তু এবং একমাত্র পরকালীন আবাসই স্থায়ী- এবং হে আমার কওম! কী আশ্চর্য! আমি তোমাদেরকে মুক্তির দিকে আহবান করছি আর তোমরা আমাকে জাহান্নামের দিকে ডাকছ! তোমরা আমাকে বলছ আল্লাহকে অস্বীকার করতে এবং তাঁর সাথে শিরক করতে যার সম্পর্কে আমার কোন জ্ঞান নেই; আর আমি তোমাদেরকে সেই সর্বশক্তিমানের দিকে আহবান করছি যিনি ক্ষমাশীল।” (৪০: ৩৮-৪২)
অতঃপর তিনি উপদেশ বাণী দিয়ে শেষ করছেন: “(এখন) আমি যা বলছি অচিরেই তা তোমরা স্মরণ করবে। আমি (আমার) যাবতীয় বিষয় আল্লাহতে অর্পণ করছি; আল্লাহ তাঁর বান্দাদের উপর সর্বদা দৃষ্টি রাখেন।” (৪০:৪৪)
বস্তুত এই পদ্ধতিই সমকালীন ইসলামী কর্মীদের দাওয়াতী কাজ চালিয়ে যাওয়া উচিত যাতে তারা একগুঁয়ে ও অন্য ধর্মের লোকদের প্রতিকূল প্রকৃতির সাথে মুকাবিলা করতে পারে। ফেরাউনের কাছে প্রেরণের সময় মূসা ও হারুন (আ)-এর প্রতি আল্লাহ যে উপদেশ দিয়েছিলেন তাতেও একই সুর ধ্বনিত : “তোমরা দ’জনেই ফেরাউনের কাছে যাও। কেননা সে সকল সীমা লংঘন করেছে। তোমরা তার সাথে নম্রভাবে কথা বলবে সম্ভবত সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা ভয় করবে (আল্লাহকে)।” (২০: ৪৩-৪৪)
অতএব হযরত মূসা (আ) ভদ্রভাবে ফেরাউনকে সম্বোধন করে বললেন, “তোমার কি আগ্রহ আছে যে, তুমি পবিত্র হও এবং আমি তোমাকে তোমার প্রভুর পথে পরিচালিত করি যাতে তুমি তাঁকে ভয় করো।” (৭৯: ১৮-১৯)
এই দৃষ্টিতে এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই যে, দাওয়াতী কাজে অভিজ্ঞ লোকেরা ভিন্নমতাদর্শী লোকদের সাথে আলাপ-আলোচনার সময় কোনো কোনো তরুণের অসহিষ্ণু আচরণকে সুনজরে দেখেন না। মানুষকে আল্লাহর পথে ডাকার সময়ে এরা প্রায়ই কর্কশ ও ক্ষিপ্ত আচরণ করে থাকে। ছোট-বড়, মাতা-পিতা, শিক্ষক, অভিজ্ঞ বুযুর্গ প্রমুখের সাথে কথা বলা বা আচরণের ব্যাপারে তাদের মান মর্যাদার দিকেও খেয়াল করা হয় না। মেহনতি মানুষ নিরক্ষর ও বিভ্রান্ত ব্যক্তিদের সাথে সম্পর্ক ও আচরণে তেমন তারতম্য দেখা যায় না। আবার রয়েছে এমন সব ব্যক্তি যারা শুধু বিদ্বেষবশত ইসলামের বিরোধিতা করে জ্ঞানের অভাবে। মোটকথা সকল শ্রেণীর লোককে তাদের নিজস্ব অবস্থানের দিকে লক্ষ্য রেখে সুযোগ ও সুবিধা মতো দাওয়াত দিতে হবে। কিন্তু আমদের সমাজে এখন এরুপ দূরদৃষ্টিসম্পন্ন লোকের বড়ই অভাব। প্রাথমিক যুগের হাদীস বিশেষজ্ঞরা অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে এ দিকে ইঙ্গিত করেছেন। যেসব রাবী নিজের রেওয়ায়েত নিয়ে আত্মপ্রচারে নেমে পড়তেন তাদের রেওয়ায়েত মুহাদ্দিসরা গ্রহণ করেননি। বরং তাদেরটাই গ্রহণ করেছেন যারা নিজেদের উদ্ভাবন সম্পর্কে ছিলেন প্রচারভিমুখ। সন্দেহ ও অবিশ্বাসও গোঁড়ামির একটি লক্ষণ। চরমপন্থীরা তাৎকষণিকভাবে একজনকে অভিযুক্ত করে বসে এবং সঙ্গে সঙ্গে রায় দিতেও তারা পারঙ্গম! “দোষ প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত একজন নির্দোষ”-এ প্রবাদটির তারা থোড়াই পরোয়া করে। তারা সন্দেহ করা মাত্র একজনকে দোষী সাব্যস্ত করে ফেলে, ব্যাখ্যা ছাড়াই উপসংহারে উপনীত হয়। তাদের দৃষ্টিতে কারো সামন্য ত্রুটি যেন মাত্রা ছাড়িয়ে যাওয়ার শামিল! সোজা কথা, ভুলেই পাপ, পাপেই কুফরী! এ ধরণের প্রতিক্রিয়া ইসলামের শিক্ষার চরম লংঘন ছাড়া আর কিছু নয়। অথচ ইসলাম চায় এক মুসলমান আরেক মুসলমানের আয়না হয়ে পরস্পরকে সংশোধন করুক; বিনম্র ও ক্ষমাশীল ব্যবহারের মধ্য দিয়ে অন্যের আচরণ ও জীবন যাত্রায় উৎকর্ষতা আনুক।
কেউ যদি ঐসব চরমপন্থীদের সাতে দ্বিমত পোষণ করে, তবে তার ধর্ম বিশ্বাস ও চরিত্রের সাধুতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়। তার মত ইসলামের দৃষ্টিতে সঠিক হলেও তাকে সীমালংঘনকারী বিদয়াতী, এমনকি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সুন্নাহর অমর্যাদাকারী বলেও চিহ্নিত করা হয়। এপ্রসঙ্গে অনেক নজীর উল্লেখ করা যায়। আপনি যদি বলেন লাঠি বহন করা বা মেঝেয় বসে খাওয়ার সাতে সুন্নাহর কোনো সম্পর্ক নেই তাহলে আপনাকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর অমর্যাদাকারী বলতে বিন্দুমাত্র বিলম্ব হবে না। অভিজ্ঞ মুসলিম মনীষী ও আলিমরাও এ অভিযোগ থেকে রেহাই পান না। কোনো ফকীহ যদি মুসলমানদের সুবিধা হতে পারে এমন কোনো ফতোয়া দেন তবে তার বিরুদ্ধে ধর্মীয় ব্যাপারে শৈথিল্যের অভিযোগ আনা হবে। যদি কোনো মুবাল্লিক যুগোপযোগী পদ্ধতিতে মানুষকে ইসলামের দাওয়াত দেন তবে তাকে পাশ্চাত্য সভ্যতার ভক্ত বলে অপবাদ দেয়া হবে। শুধু জীবিত নয়, মৃত ব্যক্তিরাও অভিযোগের হাত থেকে রেহাই পান না। অর্থাৎ চরমপন্থীদের সাথে দ্বিমত পোষণ করলেই আর রক্ষা নেই। নির্বিচারে তাকে ফ্রিম্যাসন, জাহমী অথবা মুতাযিলী বলে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হবে। এখানেই শেষ নয়, ইসলামের চার মহান ফকীহর বিরুদ্ধেও চরমপন্থীরা নির্দ্বিধায় বিষেদগার করতে কসুর করেনি।
প্রকৃতপক্ষে হিজরী চতুর্থ শতকের মুসলিম উম্মাহর সমগ্র ইতিহাসকে আক্রমনের লক্ষ্য বস্তু করা হয়। অথচ এ কালটা নজীরবিহীন সভ্যতা ও গৌরভময় অবদানের জন্যে অবিস্মরণীয়। চরমপন্থীরা এই যুগটাকে সমসাময়িক সকল অশুভ কর্মকান্ডের উৎসস্থল বলে মনে করে। কেউ কেউ এটাকে ব্যক্তিগত ক্ষমতা দ্বন্ধ সংঘাতের যুগ বলে বিশ্বাস করে। আবার কেউ বলে এটা অজ্ঞাত ও কুফরীর যুগ। এই ধ্বংসাত্মক প্রবনতা নতুন কিছু নয়। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর যামানায়ও চরমপন্থীদের অস্তিত্ব ছিল। একদা জনৈক চরমপন্থী আনসার গনিমতের মাল বণ্টনে রাসূলল্লাহ (সা)-এর বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ এনেছিলো। আধুনিক চরমপন্থীদের মারত্মক দোষ হলো সংশয়। তারা যদি কুরআন ও সুন্নাহকে সঠিকভাবে হৃদয়ঙ্গম করতো তাহলে দেখতো যে, মুসলমানদের অন্তরে পারস্পারিক বিশ্বাস ও আস্থা সৃষ্টি করাই ইসলামের লক্ষ্যে। কোনো মুসলামানের উচিত নয় আরেক মুসলমানের গুণগুলো উপেক্ষা করে তার ছোট-খাট ত্রুটিগুলো বড় করে দেখা। কুরআন বলছে: “অতএব, আত্মপ্রশংসা করো না। তিনিই সবচেয়ে ভাল জানেন কে পরহেযগার।” (৫৩:৩২)
বস্তুত ইসলাম দুটি বিষয়ে মানুষকে কঠোরভাবে হুঁশিয়ার করে দিয়েছে: আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া এবং অপরকে সন্দেহ করা। আল্লাহ তায়ালা বলেন, “হে ঈমানদারগণ! বহুবিধ অনুমান থেকে দূরে থাকো, কারণ অনুমান কোনো কোনো ক্ষেত্রে পাপ।” (৪৯:১২)
রাসূলূল্লাহ (সা) এ প্রসঙ্গে বলেন, “সংশয় থেকে দূরে থাকো, কেননা সংশয় হচ্ছে কোনো কথাবার্তার মিথ্যা দিক।” (সকল প্রমাণ্য সূত্রে সমর্থিত)
ঔদ্ধত্য, অন্যকে ঠকানোর মনোবৃত্তি ও ঘৃণা থেকেই সংশয়ের উৎপত্তি। এগুলো হচেছ অবাধ্য আচরণের প্রথম ভিত্তি আর অবাধ্যতা হচ্ছে শয়তানী কাজ। শয়তান এই দাবী করেছিলো, “আমি তাঁর (আদমের) চেয়ে ভাল।” (৩৮:৭৬)
আর এজন্য সে হযরত আদম (আ) কে সিজদা করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলো। এ ধরণের অহঙ্কারের পরিণতি সম্পর্কে হুঁশিয়ারী পাওয়া যায় এই হাদীসে:“তুমি যদি শোন যে, কেউ বলছে মানুষ ধ্বংস হয়ে গেছে তাহলে বৃথা দম্ভের জন্যে সে নিজেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।” (মুসলিম)
আরেকটি রেওয়াতে আছে : “..... সে নিজেই তাদের ধ্বংসের কারণ।” অর্থাৎ তাঁর সন্দেহ ও অহঙ্কার এবং আল্লাহর রহমত থেকে তাদেরকে নিরাশ করানোই (ধ্বংসের কারন) এমন একটি প্রবণতা যা অবয়ের সূচনা করে এবং মুসলিম মনীষীরা একে “মনের রোগ” বলে চিহ্নিত করেছেন। রাসূলুল্লাহ(সা) ও এ ব্যাপারে আমাদেরকে সতর্ক করে দিয়েছেন, “তিনটি মারাত্মক পাপ আছে- অতিরিক্ত লোভ, কামনা ও অহঙ্কার।” মুসলমান তার কোনো কাজেই অহঙ্কার করতে পারে না। কেননা সে তো এ ব্যাপারে কখনোই নিশ্চিত হতে পারে না যে, আল্লাহ তার আমল মঞ্জুর করবেন। আল্লাহ দাতা ব্যক্তিদের সম্পর্কে আলকুরআনে বলেছেন: “এসব লোক ভীতিপূর্ণ হৃদয়ে দান-খয়রাত করে। কারণ তারা তাদের প্রভুর কাছে ফিরে যাবে।” (২৩:৬০)
হাদীস শাস্ত্রে কুরআনের এই আয়াতের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে যে এরা হচ্ছে সেই সব সৎকর্মশীল লোক যারা এই ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকে যে, তাদের আমল আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নাও হতে পারে। ইবনে আতা বলেন: “আল্লাহ তোমার জন্যে আনুগত্যের দুয়ার খুলে দিতে পারেন। কিন্তু গ্রহনযোগ্যতার দ্বার নাও খুলতে পারেন। তিনি তোমাকে অবাধ্য হওয়ার পরিস্থিতির মধ্যে ফেলতে পারেন (যাতে তুমি অনুতপ্ত হয়ে) আবার সঠিক পথে ফিরে আসতে পারো। অবাধ্যতার ফলশ্রুতিতে যে বিনয়াবনত চিত্তের উন্মেষ হয় তা অহংকার ও উদ্ধতপূর্ণ সাধুতার চেয়েও উত্তম।” হযরত আলী ইবনে আবু তালিবের (রা) বাণীতে আমরা বর্ণনার প্রতিধ্বনি পাই : “ যে ভাল কাজ মানুষের মনে অহংকার আনে তার চেয়ে আল্লাহ তার উপর মুসিবতকেই পছন্দ করেন।” ইবনে মাসুদ বলেন, “ধ্বংসের দু’টি প্রধান লক্ষণ হচ্ছে অহঙ্কার ও নৈরাশ্য। অধ্যবসায় ও সংগ্রাম ছাড়া সুখ অর্জন করা যায় না। একজন অহংকারি ব্যক্তি অধ্যবসায়ী হতে পারে না। কারণ সে নিজেকে পূর্ণতাপ্রাপ্ত বলে মনে করে। আর হতাশ ব্যক্তি কোনো চেষ্টাই চালায় ন। কারণ এটাকে সে অর্থহীন মনে করে।”
আবার আসুন দেখা যাক চরমপন্থার চরম রূপ কী। চরমপন্থী গ্রুপ অন্য সকল মানুষের শান্তি ও নিরাপত্তার অধিকারী অস্বীকার করে। অতএব প্রতিপক্ষকে হত্যা এবং তার বিষয় সম্পত্তি ধ্বংস করার পন্থা বেছে নেয়। এই অবস্থা তখন সৃষ্টি হয় যখন চরমপন্থী গ্র“প তাদের বাইরে অন্য সকলকে কাফির বলে ভাবতে শুরু করে। এ ধরনের চরমপন্থার ফলে বাকী সমস্ত উম্মাহর সাথে তাদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। প্রাথমিক যুগে খারিজীরা ঠিক এমনিফাঁদে পড়েছিলো। অথচ তারা নামায, রোযা ও কুরআন তিলাওয়াতের মতো ধর্মীয় রীতিনীতি পালনে অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ছিলো। কিন্তু তাদের চিন্তাধারা ছিলো বিকৃত। তাদের বিশ্বাস ও আচরণে প্রচন্ড গোঁড়ামীর দুরুন অনিচ্ছা সত্ত্বেও সহজ সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছিলো। রাসূলুল্লাহ (সা) এদের সম্পর্কে আভাস দিয়েছিলেন এভাবে: “তাদের (আলখাওয়ারিজ) নামায, কিয়াম ও তিলাওয়াতের তুলনায় তোমাদের মধ্যে কারো নামায, কিয়াম ও তিলাওয়াত অনুল্লেখযোগ্য মনে হবে।” তথাপি তিনি তাদের সম্পর্কে বলেন, “তারা কুরআন তিলাওয়াত করবে। কিন্তু গলার বাইরে যাবে না এবং কোনো রকম স্বাক্ষর ছাড়াই তারা ধর্মের পথ অতিক্রম করবে।” (মসলিম)
রাসূলুল্লাহ (সা) আরো বলেন, “তারা মুসলমানদেরকে খতম করা এবং মুশরিকদের রক্ষা করা তাদের কর্তব্য বলে মনে করবে।” (মসলিম)
এ কারণে কোনো মুসলমান খারিজীদের হাতে পড়লে নিজেকে আল্লাহর বাণী ও কিতাব সম্পর্কে জানতে আগ্রহী মুশরিক বরে পরিচয় দিতো। একথা শুনে খারিজীরা তাকে প্রাণে বাঁচাতো এবং নিরাপদে গন্তব্য স্থানে পৌঁছার ব্যবস্থা করে দিতো। তাদের কার্যকলাপের সমর্থনে তারা কুরআনের এই আয়াতকে প্রমাণ হিসেবে দাখিল করতো: “কোনো মুশরিক আশ্রয় চাইলে তাকে আশ্রয় দাও, যাতে সে আল্লাহর বাণী শুনতে পায়, তারপর তাকে তার নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দাও। কারণ তারা জ্ঞান রাখে না।” (৯:৬)
পরিতাপের বিষয় এই যে, আটক লোকটি যদি স্বীকার করতো যে, সে মুসলমান তবে তাকে খারিজীরা হত্যা করতো। দুর্ভাগ্যজনক যে, কোনো কোনো মুসলমান এসব ঘটনা থেকে শিক্ষা নেননি। জামায়াত আত-তাকফির আল-হিজরা মনে হয় খারিজীদের পদচিহ্ন ধরেই এগোচ্ছে। যারা পাপ করে সঙ্গে সঙ্গে তওবা করে না তাদেরকে এই জামায়াত কাফির বলে মনে করে। যেসব শাসক শাসন কাজে শরীয়ত প্রয়োগ করেন না এবং যেসব শাসিত এদের আনুগত্য করে উভয়েই এদের চোখে ধিক্কৃত। আর যেসব আলিম উভয় পক্ষকে কাফির বলে নিন্দা করেন না তারাও ধিক্কৃত। যারা এই গ্রুপের কর্মসূচী প্রত্যাখ্যান করে কিংবা চার ইমামের অনুসরণ করে তাদেরকেও এরা কাফির বলে মনে করে। কেউ যদি তাদের দলে গিয়ে কোনো কারণে দল ত্যাগ করে তবে তাকে মুরতাদ বলে অবশ্যই হত্যা করা হবে। তারা ৪র্থ শতাব্দীর পরবর্তী যুগকে অজ্ঞতা ও কুফরীর যুগ বলে অভিহিত করে। এভাবে এই গ্রুপ কুফরীর অপবাদ দিতে এতোই পারঙ্গম যে, এদের হাত থেকে জীবিত মৃত কেউই রেহাই পায় না। বস্তুত এভাবে এই গ্রুপ গভীর পানিতে পড়েছে। কেননা কাউকে কুফরীর অপবাদ দেয়ার পরিণতি মারাত্মক। তার জীবন ও সম্পত্তির বাজেয়াপ্তি তখন আইনসিদ্ধ হয়ে যায়। তার সন্তান ও স্ত্রীর ওপর অধিকার থাকবে না; সে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হবে, কেউ তার উত্তরাধিকারীও হতে পারবে না; তার দাফন ও জানাযা নিয়েও সমস্যা সৃষ্টি হবে। কেননা তাকে মুসলমানদের গোরস্তানে জায়গা দেয়া যায় না ইত্যাদি ইত্যাদি!
রাসূলুল্লাহ(সা) বলেছেন, “যখন কোনো মুসলমান আরেক মুসলমানকে কাফির বলে তখন তাদের মধ্যে নিশ্চয় একজন তাই।” (বুখারী)
এর অর্থ, কুফরীর অভিযোগ প্রমাণিত না হলে যে অভিযোগ আনবে তার ওপরেই ঐ অভিযোগ বর্তাবে, যার মানে হচ্ছে ঐ ব্যক্তি দুনিয়া ও আখিরাতে কঠিন মুসিবতের সম্মুখীন হবে। উসামা বিন জায়িদ বলেন: “যদি কোনো ব্যক্তি বলে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, তাহলে ইসলামের মধ্যে দাখিল হলো এবং (ফলত) তার জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা পেয়ে গেলো। কিন্তু যদি সে ভয়ে কিংবা তলোয়ারের মুখে একথা বলে তবে তার জওয়াবদিহি আল্লাহÍ কাছেই তাকে করতে হবে। কেবল দৃশ্যমান ঘটনারই আমরা (বিচার) করতে পারি।” (বুখারী)
হযরত উসামা (রা) এক যুদ্ধে এক ব্যক্তি কলেমায়ে শাহদাত উচ্চারণ করার পরেও তাকে হত্যা করেছিলেন। ঐ ব্যক্তির গোত্র যুদ্ধে পরাজিত হয়েছিলো। রাসূলুল্লাহ (সা) এ কথা জানতে পেরে উসামার (রা) কাছে কৈফিয়ত তলব করেন। তখন তিনি বলেন, “আমি মনে করেছিলাম ঐ ব্যক্তি হয়তো আশ্রয়ের আশায় এবং ভীত হয়ে কলেমা পাঠ করেছে। ” রাসূলুল্লাহ (সা) জিজ্ঞেস করলেন, “আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই-এই স্বীকারোক্তির পরেই কি তুমি তাকে হত্যা করেছিলে? উসামা (রা) বর্ণনা করেন, “রাসূলুল্লাহ (সা) বার বার আমাকে এই প্রশ্ন করতে লাগলেন যতোক্ষণ না আমার মনে হলো এই দিনটির আগে আমি ইসলাম গ্রহণই করিনি।”
শরীয়ত আমাদেরকে এই শিক্ষা দেয় যে, যারা সচেতনভাবে ও স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেছে, সাক্ষ্য ও ঘটনাবলী দ্বারা সুপ্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত তাদেরকে ইসলাম থেকে বহিস্কৃত করা যাবে না। খুন, ব্যভিচার, মদ্যপান ইত্যাদির মতো কবীরা গুনাহ করলেই কারো বিরুদ্ধে কুফরীর অভিযোগ আনা যাবে না-অবশ্য এতটুকু দেখতে হবে যে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির শরীয়তের প্রতি অস্বীকৃতি বা অশ্রদ্ধা আছে কিনা। এ কারণে ঠান্ডা মাথায় হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তির আত্মীয় ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজনের মধ্যেও কুরআন ভ্রাতৃপ্রতিম সম্পর্ক স্থাপন করতে চায়। কুরআন বলছে: “তবে তারা ভাইয়ের তরফ থেকে কাউকে কিছু মাফ করে দেয়া হলে প্রচলিত নিয়মের অনুসরণ করবে এবং সততার সাথে তাকে তা প্রদান করতে হবে।” (২:১৭৮) যারা একজন মদ্যপায়ীকে অভিশাপ দিয়েছিলো তাদের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন: “তাকে অভিশাপ দিও না। সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা) কে ভালবাসে।” (বুখারী)
ঐ মদ্যপায়ী ইতিপূর্বে কয়েকবার মদ্যপানের অভিযোগে শাস্তি ভোগ করেছিলো। উপরন্তু খুন, ব্যভিচার ও মদ্যপানের মতো অপরাধের জন্যে শরীয়ত ভিন্ন ভিন্ন রকম শাস্তির বিধান করেছে। এগুলো যদি কুফরই হতো তবে তো তাদেরকে রিদ্দার (ইসলাম ত্যাগের) বিধি মুতাবিক দন্ড দেয়া হতো!
চরমপন্থীরা যেসব দুর্বোধ্য বায়বীয় প্রমাণের ভিত্তিতে অভিযোগ খাড়া করে, কুরআন ও সুন্নাহর মৌলিক ও দ্ব্যর্থহীন ভাষ্যে তা খন্ডন করা হয়েছে। এই বিষয়টি বহু শতাব্দী পূর্ব থেকে একটি মীমাংসিত বিষয়, অতএব এর পুনরুজ্জীবন প্রচেষ্টা নিরর্থক।
পরিভাষা সঙ্কেত
ইজমা : ইসলামী আইনের সূত্র হিসেবে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত।
আত-তাবিঈ : রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাহাবীদের সান্নিধ্য লাভকারী।
হিজাব : নারীর ইসলামী পোষাক।
আওরাহ : নারী-পুরুষের দেহের সেই অংশ বা শরীয়ত মতে অবশ্যই আবৃত রাখতে হবে।
ফাসাকা : পাপের কাজ।
আল-মুন্দুব : যে আইন ও কাজ অনুমোদিত।
কিয়াস : ইসলামী আইনের উৎস, কুরআন ও হাদীসের আলোকে যুক্তিপূর্ণ সিদ্ধান্ত।
রিদ্দাহ : (বিশেষণ, মুরতাদ) আল্লাহর আনুগত্য এবং ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিত্ব শপথপূর্বক প্রত্যাহর।
দ্বিতীয় অধ্যায়
চরমপন্থার কারণ
চরমপন্থা বা গোঁড়ামী বিক্ষিপ্ত ঘটনাবলী থেকে উৎপন্ন হয়নি। এর অবশ্যই কারণ ও উদ্দেশ্য আছে। সকল প্রণীর মতো ঘটনা ও কার্যাবলী ও শূন্য থেকেউদ্ভব হয় না- বীজ ছাড়া যেমন চারা হয় না। প্রতিটি ঘটনার পেছনে থাকে কার্যকারণ। এটা আল্লাহর সৃষ্টিরও রীতি (সুনাম)। কোনো রোগের প্রতিকার করতে হলে প্রথমে দরকার রোগ নির্ণয় (ডায়াগনোসিস)। আবার এর জন্যে অত্যাবশ্যক হচ্ছে রোগের কার গুলো জানা আর কারণ জানা না গেলে রোগের ডায়াগনোসিস অসম্বম- অন্তত খুব কষ্টকর। এ কথা স্মরণ রেখেই আমরা চরমপন্থর (গোড়ামীর) কারণ ও উদ্দেশ্য নির্ণয়ে প্রয়াসী হবো। এখানে চরমপন্থা শব্দটি গুলু অর্থাৎ ধর্মীয় বাড়াবড়ির সমার্থবোধক।
প্রথমেই আমাদেরকে বুঝতে হবে যে, কোনো একটা মাত্র কারণ গোঁড়ামী বিস্তারের জন্যে সামগ্রিকভাবে দায়ী নয়। এটা একটা জটিল অদ্ভুত বিষয়। এর পেছনে নানা পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত কারণ রয়েছে। এগুলোর কোনো কোনোটি প্রত্যক্ষ, কোনোটি পরোক্ষ, কোনোটির গোড়া সূদুর অতীতে আবার কোনোটির উৎপত্তি বর্তমানে। সুতরাং একটি বিশেষ কারণের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে অনান্য কারণগুলো উপেক্ষা করা ঠিক হবে না। কোনো কোনো মতের প্রবক্তারা এরূপ একপেশে দৃষ্টি ভঙ্গি নিয়ে বিচার বিশ্লেষণে অভ্যস্ত। উদাহরণস্বরূপ মনোবিজ্ঞানী, বিশেষত মনস্তত্ত্ববিদরা অবচেতন মন থেকে উদ্ভূত কারণগুলোর ওপর গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। অন্যদিকে সমাজ বিজ্ঞানীরা সামজিক ও পরিবেশগত প্রভাবের মুখে মানুষের অসহায়ত্বের দিকে ইঙ্গিত দেন। তাদের দৃষ্টিতে মানুষ হচ্ছে সমাজের হাতে বন্দী প্রাণহীন পুতুল। ঐতিহাসিক বস্তুবাদের প্রবক্তারা যুক্তি দেখান, অর্থনৈতিক শক্তিই ঘটনাবলীর স্রষ্টা এবং এটাই ইতিহাসের গতডি পরিবর্তন করে।
পক্ষান্তরে আরেক দল অপেক্ষাকৃত ব্যাপক ও ভারসাম্যময় দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেন। তাদের মতে কারণসমূহ অত্যাধিক জটিল ও পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। এগুলো নানবিধ ক্রিয়া উৎপন্ন করে এবং একটা থেকে আরেকটার রূপ ভিন্ন। কিন্তু শেষ বিশ্লষণে এগুলোর প্রভাব অনস্বীকার্য। গোঁড়ামির কারণসমূহ ধর্মীয়, রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, মানসিক, বুদ্ধিবৃত্তিক অথবা সবগুলোর সমন্বয়ও হতে পারে। পরিবারের সদস্যদের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে অথবা গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে সমাজে অথাৎ সেই সমাজের বিশ্বাস ও আচরণ,কল্পনা ও বাস্তব, ধর্ম ও রাজনৈতিক, কথা ও কাজ, আকাঙ্ক্ষা ও সাফল্য অথবা দ্বীন ও দুনিয়ার অসংগতির মধ্যে এর কারণসমূহ বিদ্যমান থাকতে পারে। স্বাভাবিকভাবে এসব পরস্পর বিরোধিতা বৃদ্ধরা মেনে নিলেও তা সাময়িকমাত্র।
ক্ষমতাসীন সরকারের দুর্নীতির দরুনও চরমপন্থা বিস্তার লাভ করতে পারে। তাদের স্বেচ্ছাচারিতা, স্বার্থপরতা, তোষামোদপ্রিয়তা, মুসলিম উম্মাহর শত্রুদের প্রতি সেবাদাসবৃত্তি, স্বদেশের জনগণের অধিকার হরণ ইত্যাদি মানুষের মাঝে চরমপন্হী মনোভাবের জন্ম দেয়। মারাত্মক ব্যাপার হচ্ছে, এ ধরনের ক্রিয়াকলাপ শেষ পযর্ন্ত ধর্ম ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক ছিন্ন করেছে।
গোঁড়ামির আরেকটি প্রধান কারন হচ্ছে, দ্বীন সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব অথাৎ এর উদ্দেশ্যে ও মূল চোতনার গভীর তাৎপর্য উপলদ্ধিতে ব্যর্থতা। এই উপলদ্ধির অর্থ সার্বিক অজ্ঞাতাকে বোঝায় না। সার্বিক অজ্ঞতা বাড়াবাড়ি বা গোঁড়ামির জন্ম দেয়। আসলে অল্পবিদ্যা হচ্ছে ভয়ঙ্করী। এসব লোক মনে করে সেসব কিছু জানে এবং নিজেই যেন ফকীহ। আসলে সে নানা অজীর্ণ জ্ঞানের জগাখিচুড়ি। সে বিভিন্ন খন্ডের রূপ এবং তার সাথে অখন্ডের সম্পর্ক নির্ণয়ে ব্যার্থ। ফলে তার সামগ্রিক দৃষ্টভঙ্গি কখনো পরিচ্ছন্ন হতে পারে না। অতএব তার পক্ষে কনো সুনির্দৃষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অসম্ভব। এমন ব্যক্তি যদি নিজেকে ফকীহ বলে দাবী করে তাহলে দীনের অবস্থা কী হবে! ইমাম আবু ইসহাক আশ-শাতিবী তার আল-ইতিশাম গ্রন্থে অল্পবিদ্যার বিপদ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছেন। বিদআত এবং মুসলিম উম্মাহর অনৈক্যের মূল কারণ হলো আত্মজ্ঞানের অহঙ্কার, বিশেষ করে ধর্মীয় বিষয়ে তার যথেষ্ট জ্ঞান আছে মনে করে কেউ যখন ইচ্ছা মাফিক ইজতিহাদ শুরু করে রায় দিতে থাকে তখন তাকে অবশ্যই মুবতাদী (নতুন কিছু উদ্ভাবনকারী) বলতে হবে। রাসূলুল্লাহ (সা) এ ধরনের লোক সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছেন: “আল্লাহ জ্ঞান কেড়ে নেন না জনগনের (হৃদয়) থেকে। কিন্তু যখন কোনো আলিম থাকে না তখন তিনি তা কেড়ে নেন এবং জনগণ অজ্ঞ লোকদেরকে তাদের নেতা বানাবে যারা জ্ঞান ছাড়াই রায় দেবে, সুতরাং তারাও বিপথগামী হবে, জনগণকেও বিপথগামী করবে।” (বুখারী)
এ থেকে বিজ্ঞাজনেরা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, খাঁটি আলিমরা জনগণকে বিভ্রান্ত করেন না। কিন্তু তাদের অভাবে আলিমের বিশ্বাসভাজন কখনোই বিশ্বাস ভঙ্গ করে না, কিন্তু বিশ্বাসঘাতক তা পারে। এর সাথে যোগ দিয়ে বলা যায় খাঁটি আলিম কখনোই বিদআতের জন্ম দেয়। আনাস ইবনে মালিক (রা) বর্ণনা করেন, রাবিয়া একদিন খুব কাঁদছিলেন। তার ওপর কোনো মুসিবত এসেছে কিনা জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, “না, এ জন্যে কাঁদছি যে, মানুষ তাদের কাছ থেকে ফতোয়া তালাশ করেছে যাদের কোনো জ্ঞান নেই।”
বস্তুত সার্বিক অজ্ঞতার চেয়ে অহংকারযুক্ত অল্পবিদ্যার পন্ডিত কখনোই তার সীমাবদ্ধতাকে স্বীকার করে না। এদের একটি লক্ষণ হলো এরা আক্ষরিক অর্থের প্রতি বেশী জোর দেয়, তাৎপর্য ও উদ্দেশ্য উপলব্ধির চেষ্টা করে না। আলজাহিরিয়া মতাবরম্বীরা এ ধরনের পণ্ডিতী করতো। তারা আত-তালিল ও কিয়াস অগ্রাহ্য করতো।
“সমকালীন জাহিরিয়া” মতালম্বীরা পূর্বসূরীদের পথ ধরে যুক্তি প্রদর্শন করে যে, বাধ্যতামূলক কাজকর্মের কোনো গভীর অর্থ খোঁজা উচিৎ নয়। অবশ্য নব্যজাহিরিয়ারা পূর্বসূরীদের মতো তালিল পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান করে না। আমার ও অন্যান্য আলিমের মতে ইবাদত হচ্ছে এমন বাধ্যতামূলক কর্তব্য যার কারণ ও উদ্দেশ্য কখনোই বিশ্লেষণযোগ্য নয়। তবে যেসব শিক্ষা আমাদের জীবনকে নিয়ন্ত্রন করতে চায় সেগুলো অবশ্যই বিশ্লেষণ করতে হবে।
সুতরাং কোনো মুসলমান দান-খয়রাত করে বলে তার হজ্জ করা উচিত কিংবা হজ্জের সময় কুরবানীর অর্থ সদকা করে দেয়া উচিত-এই দাবী করা ভুল হবে। তেমনিভাবে এটাও অচিন্তনীয় যে, আধুনিক কর যাকাতের স্থান দখল করবে, রমযানের পরিবর্তে অন্য যে কোনো মাসে রোযা কিংবা শুক্রবারের স্থলে অন্য যে কোনো দিন জুমআ’র নামায আদায় করা যাবে। এসব বাদ দেওয়া যাবে না। এগুলো সবই মুসলমানের জন্যে অবশ্য পালনীয়। কিন্তু এ ধরনের আনুষ্ঠানিক ইবাদত প্রক্রিয়া ব্যতীত অন্য যে কোনো বিষয়ের কারণ ও উদ্দেশ্য আমরা বিশ্লেষণ করতে পারি এবং সঠিক উপলব্ধির পর ইতিবাচক অথবা নেতিবাচক সিদ্ধান্ত নেয়া যেতে পারে।
এখন আমরা কতিপয় প্রামাণিক বিষয় পর্যালোচনা করতে পারি:
ক. একটি বিশ্বস্ত হাদীসে বলা হয়েছে, কাফিরের দেশে কুরআন শরীফ নিয়ে যাওয়া উচিত নয়। এই নিষেধাজ্ঞার কারণ পরীক্ষা করলে দেখা যাবে, কাফিররা কুরআনের ক্ষতি বা অবমাননা করতে পারে এই আশংকায় রাসূলুল্লাহ (সা) এরূপ আদেশ দিয়েছেন। এরূপ আশংকা না থাকলে যেখানে ইচ্ছে কুরআন শরীফ নেয়া যেতে পারে। তাছাড়া দাওয়াতী কাজের জন্যে এটা তো অপরিহার্য।
খ. আরেকটি হাদীসে মাহরাম (অথাৎ বিষয় অযোগ্য পুরুষ আত্মীয়) সঙ্গী ছাড়া মুসলিম নারীকে সফর করতে নিষেধ করা হয়েছে। নারীর নারাপত্তা ও সফরের কষ্ট লাঘবই এর উদ্দেশ্য। আধুনিক যুগে যেহেতু সফরের এতো ঝুঁকি নেই তাই কোনো স্বামী তার স্ত্রীকে গাড়িতে তুলে দিতে পারেন। গন্তব্য স্থানে কোনো মাহরাম ব্যক্তি তাকে স্বাগত জানালে দোষের কিছু নেই। বস্তুত রাসূলুল্লাহ (সা) যোগাযোগ ব্যবস্থার এরূপ উন্নতির আভাস দিয়ে বলেছিলেন, এমন এক সময় আসবে যখন মানুষ এক আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় না করেই ইরাক থেকে মক্কা ভ্রমন করতে পারবে।
গ. রাসূলুল্লাহ (সা) দীর্ঘ অনুপস্থিতির পর রাতে বাড়ি ফেরা নাষিদ্ধ করেছেন। তিনি নিজেও সক্লে বা সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরতেন। এর দু’টো কারণ। প্রথম, আকস্মিকভাবে স্বামীর রাতে বাড়ি ফেরার মধ্যে স্ত্রীর প্রতি অবিশ্বাস ইসলাম সমর্থন করে না। দ্বিতীয়ত, স্ত্রী যেন নিজেকে পরিপাটি করে রাখতে পারে সে জন্যে স্বামীর আগমনের সময় জানার অধিকার তার আছে। কিন্তু এখন এসব আনুষ্ঠানিকতার সুযোগ খুব কম। মানুষের যাতায়াতের সময়সূচী মেনে চলতে হয়। কে কখন কোথায় যাবে তা আগেভাগেই নিশ্চিত করে বলা যায় না। তবে বাড়ি যাওয়া আগে টেলিফোন বা চিঠিতে জানানো উচিত। সুতরাং আমাদেরকে স্থান ও কালের প্রেক্ষাপটে উক্ত নিষেধাজ্ঞার কারণ ও উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ করতে হবে।
যাকাতকে ইবাদত মনে না করে অনেকে এটাকে কেবল অর্থ ব্যবস্থার অংশ হিসেবে গণ্য করতে চান। যাকাত ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এবং ধর্মীয় কর্তব্য। এটা ইসলামী শরীয়ত ব্যবস্থার একটি তাৎপর্যপূর্ণ ও স্থায়ী আয়ের সূত্র, সেই হিসেবে ইসলামী অর্থ ব্যবস্থারও স্তম্ভ। তাই এটার বাধ্যবাধকতাকে খর্ব করার কোনো উপায় নেই। যাকাতের সামাজিক সম্ভাবনার দিকে লক্ষ্য করে সকল মাযহাব-এর আহকামের ব্যপারে যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আমি ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বাস করি, ফসলের (ফল ও শস্য) দ অথবা পাঁচ ভাগ গরীবদের দান করা বাধ্যতামূলক- সে ফসল শুকনোই হোক আর তাজা হোক। সামাজিক অর্থনৈতিক বিকাশ হচ্ছে - এর মূল লক্ষ্য। ধনীর সম্পদে গরীবের সুনির্দিষ্ট হিস্যা আছে। আর এর লক্ষ্য হচ্ছে পবিত্রতা ও বিশুদ্ধতা: “তাদের সম্পদ থেকে তুমি সাদকা গ্রহন করো। এর দ্বারা তুমি তাদেরকে পরিশুদ্ধ ও পবিত্র করবে।”
একজন আধ্রনিক পন্ডিত “খাদ্যশস্যের ওপর সাদকা নেই” এই হাদীস উদ্ধৃত করে উপরোল্লিখিত যুক্তি অস্বীকার করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আমলে খাদ্যশস্যের ওপর যাকাতের বিধান প্রচলিত ছিল না বলেও তিনি দাবী করেন। কিন্তু হাদীসটি দুর্বল বিধায় তার যুক্তি মিথ্যা এবং বলেছেন এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহর (সা) কোনো প্রামাণিক হাদীস নেই। দ্বিতীয় যুক্তিটিও দু’টি কারণে মিথ্যা। প্রথম কারণ, ইমাম ইবনুল আরবীর ভাষায় এ প্রসঙ্গে কুরআন শরীফে বর্ণিত সুস্পষ্ট বিধানের মুকাবিলার অন্য কোনো প্রমাণ অগ্রাহ। কুরআন বলছে : “মৌসুমের ফলমূল থেকে খাও; কিন্তু ফসল সংগ্রহের দিনে ন্যায্য হিস্যা দান করে দাও।” (৬ : ১৪১)
দ্বিতীয় কারণটি হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জীবদ্দশায় এ ব্যবস্থার প্রচলন না থাকলেও আমাদেরকে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হবে যে, তিনি হয়তো বিষয়টি তাঁর উম্মতের বিবেকের ওপর ছেড়ে দিয়েছেন। কেননা সে যুগে ফলমূল ও খাদ্যশস্য সংরক্ষণ করা কষ্টকর ছিলো।
অবশ্য উক্ত পন্ডিত স্বীকার করেছেন যে, একটি হাদীসে কেবল খেজুর, গম, কিসমিস ও বার্লির ওপর যাকাত সীমাবদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু এ হাদীসটিও দুর্বল এবং কোনো কোন হাদিস বিশারত এর প্রামাণিকতা স্বীকার করেননি বিধায় কোনো মাযহাব একে প্রমাণিক বলে গ্রহণ করেনি। সুতরাং সকল ফলসের ওপর যাকাতের বাধ্যতামুলক বিধানকে কিভাবে অস্বীকার করা যায় যখন কুরআন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলছে : “তিনিই লতা ও বৃক্ষ উদ্যানসমূহ সৃষ্টি করেছেন এবং খেজুর বৃক্ষ বিভিন্ন স্বাদ বিশিষ্ট খাদ্য শস্য, জলপাই ও ডালিম র্সষ্টি করেছেন। এগুলো একে অন্যের সদৃশ এবং বিসদৃশও। যখন এটা ফলবান হয় তখন ফল খাবে আর ফসল তুলবার দিনে এর দেয় প্রদান করবে। ” (৬:১৪১)
আরেকটি আয়াতে বলা হয়েছে: “হে ইমানদারগন, তোমরা যা কিছু উপার্জন করো এবং আমি যা ভূমি থেকে তোমাদের জন্য উৎপাদান করে দিই তার মধ্যে যা উৎকৃষ্ট তা ব্যয় করো।” (২:২৬৭)
একটি প্রমানিক হাদীসেও যাকাত প্রদানের বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হিয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, “নদী অথবা বৃষ্টির পানি বিধৌত জমি থেকে এক-দশমাংশ; (সেচের) পানি সিঞ্চিহত জমি থেকে শতকরা পাঁচ ভাগ।” (ইমাম আবু হানিফা: আহকামুল কুরআন)
এই হাদীসে কোনো বিশেষ ফসলের মধ্যে যাকাতকে সীমিত করা হয়নি। এখানে বাধ্যতামূলক হার পরিষ্কারভাবে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। পরবর্তীকালে উমর ইবনে আবদুল আজিজ ও ইমাম আবু হানিফা (রহ) এ ব্যাপারে কুরআনী আয়াতের (৬:১৪১)
ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে ইমাম আবু হানিফা (রহ)-র মতগুলোকে অপেক্ষাকৃত সুদৃঢ় বলে উল্লেখ করেছেন। অনান্য মাযহাবের প্রমাণগুলোকে দুর্বল আখ্যায়িত করে ইবনুল আরবী (রহ) বলেছেন, “ আবু হানিফা (রহ) (পূর্বোউল্লিখিত) মূল সূত্রগুলোকে আয়নার মত ব্যবহার করেসত্যকে অবলকন করেছেন।” শরাহ আত-তিরিমিযীতে আরবী (রহ) বলেন, “(যাকাতের ব্যাপারে) আবু হানিফা (রহ)-এর মাযহাব সূদৃঢ় প্রমাণ পেশ করেছে।” আহকাম ও তাদের কারনগুলোর মধ্যেকার সঙ্গতি উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হলে মারাত্মক স্ববিরোধিতার আশংকা থাকে। তখন আমরা একই বিষয়কে ভাগ ভাগ করে দেখি। আবার বিভিন্ন বিষয়কে এক করে ফেলি। এটা হচ্ছে সুবিচারের পরিপন্থী যার ওপরে আশ-শারীরাহ প্রতিষ্ঠিত পাণ্ডিত্যভিমানীরা কোনো জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি ছাড়াই আহকামের কারন খুঁজতে গিয়ে বিষয়গুলোকে জটিল করে তোলেন। এ জন্যে জনগণের কছে সত্য স্পষ্ট করে তুলে ধরতে আমাদের প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে অথবা বিজ্ঞ ও যোগ্য ব্যক্তিদের জন্যে ইজতিহাদের দ্বার খুলে দিতে হবে। সেই অনধিকার চর্চাকারী পরজীবীদের বিরুদ্ধেও সতর্ক থাকা দরকার।
১. ছোট খাট বিষয় নিয়ে মেতে থাকা
বুদ্ধিবৃত্তিক বন্ধাত্বের একটি লক্ষন হচ্ছে বড় বড় বিষয় উপেক্ষা করে ছোটখাট বিষয় নিয়ে মেত থাকা। অথচ বৃহৎ বিষয়গুলৌ এতো গুরুত্বপূর্ন যে, এগুলোর প্রতি উদিসীন উম্মাহর অস্তিত্ব, আশা-আকাক্ষা, পরিবেশ তথা সামগ্রিক সত্তাকে বিপন্ন করতে পারেঅ দাড়ি রাখা, গোড়ালীর নিচে পযর্ন্ত কাপড় পরা, তাশাহুদের সময় আঙ্গুল নাড়ানো, আলৌকচিত্র রাখার মতো ছোটখাট বিষয়গুলো নিয়ে অবিরাম বাড়াবাড়ি চলছে।এমন এক সময় এসব নিয়ে হৈ চৈ করা হচ্ছে যখন মুসলিম উম্মাহ ধর্ম নিরপেক্ষবাদ, ইহুদীবাদ ও খৃষ্টবাদের নিরবচ্ছিন্ন বৈরিতা ও অনুপ্রবেশের সম্মুখীন। ক্রীশ্চান মিশনরীরা মুসলমানদের ঐতিহাসিক ও ইসলামী চরিত্র ক্ষুণ্ণ করার জন্যে নতুন ক্রুসেড শুরু করেছে। দুনিয়ার বিভিন্ন আংশে মুসলমানদেরকে নির্মমভাবে হত্যা করা হচ্ছে। মুসলিম ধর্ম প্রচারকরা চরম ভীতি ও নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন। আমি দেখছি, যারা শিক্ষাদীক্ষা আথবা জীবিকা অর্জনের জন্যে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও ইউরোপে এসেছেন, তাঁরাও ছোটখাট বিতর্কিত বিষয়গুলো সাথে নিয়ে এসেছেন এবং এ নিয়ে মাথা ঘামান। এটা এক কথায় র্মমান্তিক! আমি নিজে দেখেছি এবং শুনেছি এসব বিষয় নিয়ে উত্তপ্ত বিতর্ক হয়েছে যে, শেষ পর্যন্ত মুসলমানদের মধ্য অনৈক্য ও বিভেদ সৃষ্টি হয়েছে। অথচ বিষয়গুলো ইজতিহাদ সাপেক্ষ। এগুলো এমন বিষয় যা নিয়ে ফকীহদের মত সর্বস্মত হয় না। আমি নিজেও এগুলের ওপর বক্তব্য রেখেছি। যা হোক এসব নিরর্থক মাসলা-মাসাকয়েল নিয়ে ঝগড়া-বিবাদ না করে প্রবাসীদের উচিত ইসলামের মূল সত্যকে আঁকড়ে ধরা। বিশেষ করে মুসলিম তরুণদের এদিকে আকৃষ্ট করা, তাদেরকে অবশ্য পালনীয় কাজগুলো করতে এবং কবীরা গুনাহ থেকে বিরত থাকতে উদ্বুদ্ধ করা। এই দায়িত্ব পালনে সফল হলে ইসলাম প্রচারে এক নতুন আশার সঞ্চার হেব।
এটা দুঃখজনক যে, যারা এ ধরনের বিতর্ক ও সংঘাতের সূত্রপাত করেন তারাই অনেক গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় বিধি পালনে উদাসীন বলে অভিযোগ রয়েছে। মাতা-পিতার প্রতি কতব্য, স্ত্রী ও সন্তান প্রতিপালন, প্রতিবেশির সাথে সদ্ভাব, সঠিকভাবে নিজ দায়িত্ব পালন, বৈধ ও অবৈধ বিচারে সতর্কতা ইত্যাদি প্রশ্নে তাদের বিরুদ্ধে অবহেলার অভিযোগ শোনা যায়। কিন্তু তারা নিজেদের মান উন্নত করার পরিবর্তে বিতর্ক সৃষ্টি করে খুব মজা পান। শেয় পর্যন্ত তাদেরকে এর দরুন বৈরিতা অথবা মুনাফিকীর ন্যায় আচরণ করতে হয়। একটি হাদীসে এরূপ বাক-বিতন্ডার কথা উণ্ণখ করা হয়েছে : “যারা (সঠিক) পথ পেয়েছে তারা কখনো বিভ্রান্ত হবে না যতক্ষন না তারা বাক-বিতন্ডায় নিমজ্জিত হয়।” (আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিযী) এ রকমও দেখা যায়, কেউ কেউ আহলে কিতাবদের জবাই করা পশুর গোশত মুসলমানদেরকে খেতে নিষেধ করেন যদিও বর্তমান ও অতীতে এর বৈধ হওয়া সম্পর্কে ফতোয়া আছে। অথধচ এ রকম লোকদেরই দেখা যাবে এর চেয়ে বড় বড় নিষিদ্ধ কাজ করতে তারা সিদ্ধহস্ত। যুক্তরাষ্ট্রে এ ধরনের একটা ঘটনার কথা আমি শুনেছি। এক ব্যক্তি খুব বড় গলায় বলছিল ইহুদী ও খৃষ্টানদের জবাই করা পশুর গোশত খাওয়া যাবে না। কিন্তু সে নির্লজ্জের মতো অন্যদের সাথে একই টেবিলে বসে মদ সহযোগে ঐ গোশত ভক্ষণ করছিলো। অথচ সে নির্দ্বিধায় একিট অনিশ্চত ও বিতর্কিত বিষয়ে গোঁড়া বক্তব্য রাখছিলো। ঠিক এ রকম পরস্পর বিরোধী আচরণ দেখে একবার হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। হযরত হুসাইনের (রা) শাহাদাতের পর ইরাক থেকে এক ব্যক্তি এসে তাকে মশা মারা হালাল কি হারাম জিজ্ঞেস করলো। ইমাম আহমদ তাঁর মসনদে বর্ণনা করছেন:
আমি ইবনে উমরের সাথে বসেছিলাম। একিট লোক এসে তাকে মশার রক্ত সম্পর্কে জিজ্ঞস করলো। ইবনে উমর (রা) তাকে বললেন, “তুমি কোত্থেকে এসেছ?” সে জবাব দিল, “ইরাক থেকে।” তখন ইবনে উমর বললেন, “দেখ লোকটির দিকে! সে আমাকে মশার রক্ত সম্পর্কে প্রশ্ন করছে, অথচ তারা (ইরাকিরা) রাসূলুল্লাহ (সা)- এর পৌত্রকে [আল-হুসাইন ইবনে আলী (রা)] হত্যা করেছে। আমি রাসূলুল্লাহ (সা) - কে বলতে শুনেছি : “তারা (হাসান ও হুসাইন) এই জগতে আমার দু’টি মিষ্টি মধুর সুরবিত ফুল।” (আহমাদ)
২. নিষেধাজ্ঞা নিয়ে বাড়াবাড়ি
ইসলামী আইনশাস্র ও শরীয়াহর জ্ঞানের অবাবে নিষেধাজ্ঞার ক্ষেত্র নিয়ে অধিক বাড়াবাড়ি দেখা যায়। কুরআন ও সুন্নায় এর বিরুদ্ধে পরিস্কার সতর্ক বাণী রয়েছে। কুরআন বলছে :
“তোমাদের মুখ থেকে যেসব মিথ্যা বের হয়ে আসে তেমনি করে তোমরা আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে বলো না যে, এটি হালাল এবং ওটি হারাম।” (১৬: ১১৬)
রাসূলুল্লাহ (সা) - এর সাহাবী এবং প্রাথমিক যুগোর বুজর্গানে দ্বীন নিশ্চত না হওয়া পর্যন্ত কনো জিনিসকে নিষিদ্ধ বা হারাম বলে ফতোয়া দিতেন না। কিন্তু চরমপন্থীরা তাৎক্ষণিকভাবে হারাম ফতোয়া দিতে যেন এক পায়ে খাড়া থাকে। ইসলামী আইনশাস্ত্রে কোন বিষয়ে যদি দুটো মত থাকে যদি এক পক্ষ বলে মুবাহ, আন্য পক্ষ বলে মাকরূহ; চরমপন্থীরা এক্ষেত্রে মাকরূহকে সমর্থন করে পরহেযগারী যাহির করে। এক পক্ষ যদি একটি বিষয়কে মাকরূহ এবং অন্য পক্ষ হারাম বলে ঘোষণা করে সে ক্ষেত্রে গোঁড়া ব্যক্তিরা হারামের পক্ষ নিয়ে সাধুতার প্রমাণ রাখতে চায় অর্থাৎ সহজ ও কঠিনের মধ্যে তারা শেষোক্তটাকে বেছে নেয়াই অধিকতর তাকওয়ার লক্ষণ বলে মনে করে। তারা ইবনে আব্বাসের (রা) কঠোর মত গ্রহণে বেশি আগ্রহী। বস্তুত এই প্রবণতা মধ্যমপন্থার দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে তাদের অজ্ঞতারই ফসল। বিষয়টি বোঝায় সুবিধার্থে আমি একটি প্রত্যক্ষ ঘটনার উল্লেখ করতে চাই।
একদিন এক গোঁড়া লোক অপর এক ব্যক্তিকে দাঁড়িয়ে পানি পান করতে দেখে তার পাক সাফ হওয়ার
জন্যে তৎক্ষণাৎ বমি করতে বলল। আমি তখন গোঁড়া লোকটিকে নম্রবাবে বললাম, “এজন্য এতো কঠোর ব্যবস্থার দরকার পড়ে না। এটা একটা চোট ব্যাপার।” সে বলল, হাদীসে এটা স্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ। আর কেউ যদি ভুলক্রমে করে বসে তবে সহীহ হাদীসে বমির বিধান আছে।” আমি জবাব দিলাম, “কিন্তু দাঁড়িয়ে পানি খাওয়ার পক্ষে যে হাদীস আছে তা অধিক প্রমাণিত এবং বুখারীর একটি অধ্যায় আছে যার শিরোনাম হলো, “দাড়িয়ে পানি পান করা।” ঐ ব্যক্তি নিষিদ্ধ হওয়ার পক্ষে কোনো হাদীসের উদ্ধৃতি দিতে পারলো না। অথচ এটা সত্য যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বিদায় হজ্জের সময় দাঁড়িয়ে পানি পান করেছিলেন। (বুখারী, মুসলিম)
এছাড়া একবার হযরত আলী (রা) দাঁড়িয়ে পানি পান করতে করতে বলেছিলেন, “এটা অনেকেই পছন্দ করে না, কিন্তু আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে এরূপ করতে দেখেছি যেমন তোমরা আমাকে দেখছ।” (বুখারী, মুসলিম)
ইবনে উমরের (রা) উদ্ধৃতি দিয়ে ইমাম তিরমিযী বলছেন, “রাসূলুল্লাহ (সা)-এর যুগে আমরা চলন্ত অবস্থায় খাবার খেতাম এবং দাঁড়িয়ে পানি পান করতাম।” কাবশাহ (রা) বলেন, “আমি একবার রাসূলুল্লাহ (সা) -কে ঝুলন্ত মশক থেকে পানি পান করতে দেখেছি।”
মোটকথা নির্ভরযোগ্য হাদীস বিশারদদের ব্যাখ্যা থেকে আমরা দেখতে পাই বসে পানি পান করাকে উৎসাহিত করা হয়েছে বটে, কিন্তু দাঁড়িয়ে পান করতে নিষেধ নেই। আর দু’টো ব্যাপারই প্রমাণিত। অতএব, কেউ দাঁড়িয়ে পান করলেও নিষেধ নেই। কেউ দাঁড়িয়ে পানি পান করলেই বমির বিধান জারি করাটা সম্পুর্ণ ভুল।
একইভাবে, আজকাল অনেক তরুণ ইসলামী পোশাক নিয়ে জল্পনা কল্পনায় লিপ্ত। হাদীসে এর দৃঢ় ভিত্তি আছে: “(পোশাকের) যে অংশ গোঁড়ালির নিচে (ঝুলে থাকে) তা আগুনে (পুড়বে)।” (বুখারী)
এ জন্য অনেক তরুণকে গোঁড়ালির উপরে পোশাক পরতে দেখা যায় এবং তাদের সঙ্গী-সাথীদের উপরেও এটা চাপাতে চায়। কিন্তু এরূপ চাপাচাপির ফলটা এই হবে যে, একপক্ষ অপরপক্ষের বিরুদ্ধে নিশ্চিতভাবেই গোঁড়ামির অভিযোগ আনবে। এটা সত্য যে, কিছু হাদীসে গোড়ালির নিচে কাপড় পরিধানের বিরুদ্ধে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। আবার অন্য হাদীসে এই নিষেধাজ্ঞার কারণ খুঁজে পাওয়া যায়। একদা এভাবে কাপড় পরাকে অহঙ্কার, ঔদ্ধত্য ও অপচয়ের লক্ষণ মনে করা হতো। দৃষ্টান্তস্বরুপ রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, “আল্লাহ কিয়ামতের দিনে সেই ব্যক্তির দিকে থাকবেন না যে অহঙ্কারবশত তার কাপড়কে (পেছনে) টেনে নিয়ে যায়।” (মুসলিম)
হযরত আবু বকর (রা) রাসুলুল্লাহ (সা)-কে বললেন, “আমার ইজার অসাবধানতাবশত নিচে নেমে যায়।” রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন “যারা গর্বোদ্ধত হয়ে এরূপ করে তুমি তাদের মধ্যে নও।” (বুখারী) এ কারনে আন-নববী ও অন্যান্য মুসলিম মনীষীরা তম প্রকাশ করেছেন যে, এরূপ কাপড় পরা মাকরূহ। কিন্তু মাকরূহ অনিবার্য কারণে মুবাহ হতে পারে।
৩. ভ্রান্ত ধারণা
ইসলামের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিক সম্পর্কে অগভীর জ্ঞান থেকেই মূলত বিতর্কের সূত্রপাত। এ জন্যে ইসলাম, ঈমান, কুফর, নিফাক ও জাহিলিয়াত ইত্যাদির সঠিক সংজ্ঞা ও পূর্ণ ব্যাখ্যা প্রয়োজন। ভাষাগত জটিলতা, বিশেষত আরবী ভাষায় ব্যুৎপত্তির অভাব বহুলাংশে বিভ্রান্তি ও ভ্রান্ত ধারণার জন্যে দায়ী। ফলত অনেকেই রূপক ও প্রকৃত অর্থের মধ্যে তারতম্য উপলদ্ধি করতে পারেন না। ঈমান ও পূর্ণ ইমান, ইসলাম ও প্রকৃত ইসলাম, বিশ্বাসে মুনাফেকী ও কর্মে মুনাফিকী, ছোট ছোট শিরক ও বড় বড় শিরকের মধ্যে তারা পার্থক্য করতে অক্ষম। এখন আমি এসব বিষয়ের একিট সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিচ্ছি। এতে এ সম্পর্কে আমারা সতর্ক হতে পারব। বস্তুত অনুভূতি, কথা ও কাজের সমন্বয়ে ঈমান পূণৃ রূপ লাভ করে।
কুরআনে এই ঈমান সম্পর্কে বলা হয়েছে :
“মুমিন তো তারাই যাদের হৃদয় কম্পিত হয় যখন আল্লাহকে স্মরণ করা হয় এবং যখন তাঁর আয়াত তাদের নিকট পাঠ করা হয়, তখন তা তাদের ঈমান আরো বৃদ্ধি করে দেয়।” (৮:২)
“সেসব ঈমানদারই সফলকাম হয়েছে যারা বিনয়াবনত চিত্তে নামায আদায় করে।” “তারাই ঈমানদার যারা আল্লাহ ও রাসূলের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং তারপর কখনোই সন্দেহ পোষন করেনি এবং আল্লাহর রাস্তায় জান ও মাল দিয়ে লড়াই করেছে। তারাই সত্যনিষ্ঠ।” (৪৯: ১৫) নিম্মোক্ত হাদীসেও ঈমানের এই রূপ তুলে ধরা হয়েছে:
“যারাই আল্লাহ ও কিয়ামত দিবসের ওপর ঈমান এনেছে তাদের উচিত আত্মীয়-স্বজনের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা ... যা ভাল তাই তাদের বলা উচিত নতুবা চুপ থাকা (উত্তম)।” (বুখারী)
আরেকটি হিদীসে ঈমানের নেতিবাচক দিক তুলে ধরা হয়েছে : “সেই ব্যক্তি ঈমানদার হবে না যতক্ষণ না সে তার (মুসলমান) ভাইয়ের জন্যে তাই ভাল মনে করবে যা সে তার নিজের জন্য ভাল মনে করেব।” (বুখারী)
এখানে লক্ষণীয়, শোষোক্ত হাদীসে দু’টিতে ঈমানের নেতিবাচক রূপ তুলে ধরে প্রকুতপক্ষে ঈমানের পূর্ণ রূপ তুলে ধরা হয়েছে।; সেরূপ ঈমান নয় যেমন বলা হয়: “যে তার জ্ঞান কাজে লাগায় না সে বিদ্বান নয়।” এখানে সীমিত জ্ঞান নয়, বরং পূর্ণ জ্ঞানের নেতিবাচক দিকটির প্রতি ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। এই হাদীসেও পূর্ণ ঈমানের পরিচয় বিধৃত হয়েছে: ঈমানের সত্তরটি শাখা আছে, তার মধ্যে একটি শাখা হচ্ছে লজ্জা বা হায়া। ইমাম আবু বকর আল-বয়হাকী তাঁর ‘আল -জামি’লী শুয়াব আল- ঈমান’ কিতাবে ঈমনকে একটি গাছের সাথে তুলনা করা হয়েছেন। গাছের কান্ড হচ্ছে ঈমানের মৌলিক অঙ্গের প্রতীক। যেহেতু গাছ এর কিছু শাকা-প্রশাখা নিয়ে ইসলামের আওতায় তাকতে পারে। ফেরেশ্তা ও তকদীরের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা।”
আল-হাফিজ আল-বায়হাকী ফতহুল বারীতে লিখেছেন: “আমাদের বুজর্গ পূর্বপুরুষরা বলেছেন : ঈমান হলো হৃদয়ে বিশ্বাস স্থাপন, মুখে উচ্চারণ ও কর্মে রূপায়ণ। এর অর্থ বাস্তব জীবনে রূপায়ণ ছাড়া ঈমান পূর্ণ হতে পরে না। এ জন্যে তারা মনে করতেন ঈমান বাড়াতে ও কমাতে পারে। আল-মাজিয়াহ মনে করেন, ঈমান শুধু মনে ও উচ্চারণে; আল-করামিয়াহ বিশ্বাস করেন, উচ্চারণই যথেষ্ট; আল-মুতাযিলাহর ধারণা, ঈমান হলো বিশ্বাস, উচ্চারন ও বাস্তাবায়নের সমন্বত রূপ।... এ ব্যাপারে তাঁদের ও পূর্ববতী বুজর্গদের মধ্যে পার্থক্য এটাই যে, পূর্বোক্তরা আমলকে ঈমানের প্রমাণ হিসেবে মনে করেন। আর শেষোক্তরা আমলকে পূর্ণতার শর্ত হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু পূর্ণ সত্তা কেবল আল্লাহ তায়ালাই। আমাদের কাছে ঈমানের মৌলিক ঘোষণাই যথেষ্ট। কেননা পরিপূর্ণ পরম সত্তা কেবল আল্লাহ জাল্লা জালালুহু। একবার যে মুখে ঈমানের ঘোষনা দেয় তখন থেকেই আল্লাহ শানুহুর দৃষ্টিতে তাকে মুসলমান হিসেবে গণ্য করা হয। যতোক্ষণ না সে এমন আচরন করে যাতে মনে হয় সে বেঈমান, যেমন মূর্তির কাছে মাথা নত করা। কেউ যখন পাপ কাজ করে তখন তাকে আমরা ঈমন সংক্রান্ত স্ব স্ব ধারণার আলোকে ঈমানদার ভাবতে আবার নাও ভাবতে পারি। পূর্ণ ঈমানদার। কারো বিরুদ্ধে যদি কাফির হওয়ার অভিযোগ ওঠে তবে এ কারণেই যে সে কুফরীর আচরণ করে।’
একজন কাফির যখন এই সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, মুহাম্মদ (সা) তাঁর রাসূল, তখুনি সে মুসলমান হয়ে যায। তৎখণাত সে নামায আদায় করলো কিনা সেটা বড় কথা নয়। যাকাত ইত্যাদি এগুলো সে মেনে নিলো সেটাই বড় কথা। আমল কতটুকু করলো সেটা পরে লক্ষণীয়। কালেমার মৌখিক উচ্চারণের সাথে সাথেই সে জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা পেয়ে গেলো। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, “যারা কালেমা (শাহাদাত) উচ্চারণ করলো, তারা আমার কাছ থেকে জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা পেলো... তাদেরকে আল্লাহর কাছেই জবাবদিহি করতে হবে।” (বুখারী)
ইসলাম শব্দটিও ইবনে উমর (রা) বর্নিত পাঁটি স্তম্ভেকেই বোঝায়: “ইসলাম পাঁচটি স্তম্ভের ওপর প্রতিষ্ঠিত - এই সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই, মুহাম্মদ (সা) তাঁর রাসূল; নামায আদায় করা যাকাত দেয়া, রোজা রাখা এবং হজ্জ আদায় করা।” হাদীস শাস্ত্রেও জিবরাঈল (আ)-এর মুখে ইসলামের সংঙা দেয়া হয়েছৈ। রাসূলুল্লাহ (সা) যখন তাঁকে বলেন, “ইসলাম কী?” তখন তিনি বলেন, “আল্লাহর ইবাদত করা এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক না করা, নামায আদায় করা যাকাত দেয়া এবং রমযান মাসে রোজা রাখা।” (বুখারী)
জিবরাঈল (আ) এর কথা থেকে আমরা ঈমান ও ইসলামের পার্থক্য বুঝতে পারি। এটাও পিরষ্কার যে, দু’টি শব্দকে এক অর্থেও ব্যবহার করা যায়। দু’টির একত্র সমাহারে দেখা যাবে একটির মধ্যে আরেকটির অর্থ লুক্কায়িত আছে, অথাৎ ঈমান ছাড়া ইসলাম নেই। ইসলাম ছাড়া ঈমান নেই। ঈমনের স্থান হৃদয় কন্দরে আর ইসলামের রূপায়ণ হচ্ছে আবেগ ও আচরণের সংমিশ্রণে। নিম্মোক্ত হাদীস থেকে আমরা এটাই উপলব্ধি করতে পারি: “ইসলাম হচ্ছে প্রকাশ্য আর ঈমান হচ্ছে অন্তরে (বিশ্বাসের বিষর)।”(আহমদ, আলবাজ্জাজ)
ঈমানের এই সংজ্ঞা আমরা কুরআনেও দেখতে পাই : “বেদুঈনরা বলে, ‘আমরা ঈমান আনলাম; বল, তোমরা ঈমান আননি বরং, তোমরা বল, আমরা আত্মসমর্পণ করেছি, কেননা তোমাদের হৃদয়ে এখনও ঈমান প্রবেশ করেনি।” (৪৯:১৪)
আর ইসলামের পূর্ণ পরিচয় দিয়ে হাদীসে বলা হয়েছে: “ইসলাম হলো (সেই অবস্থা) যখন তোমার হৃদয় (সম্পূর্ণরূপে) আল্লাহ্ র কাছে সমর্পিত হয় এবং যখন তুমি মুসলমানদেরকে তোমার যবান ও হাত দিয়ে ক্ষতি করা থেকে বিরত থাকো।” অন্য দু’টি হাদীসেও বলা হয়েছে: “সেই হচ্ছে মুসলমান যার যবান ও হাত দিয়ে অন্য মুসলমানের ক্ষতি হয় না” এবং তুমি নিজের জন্য যা ইচ্ছে করো অপরের জন্যে তাই করলেই তুমি মুসলমান।”
ফিকাহর ভাষায় কুফরের অর্থ হচ্ছে আল্লাহ ও তাঁর কালামের প্রতি অকৃতজ্ঞতা ও অস্বীকৃতি। আল-কুরআনে এর প্রতিধ্বনি শোনা যায়: “কেউ আল্লাহ্, তাঁর ফেরেশতা, তাঁর কিতাব, তাঁর রাসূল এবং কিয়ামত দিবমকে অস্বীকার করলে সে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে।” (৪:১৩৬)
কুফর রিদ্দাকেও বোঝায় ফলশ্রুতিতে ঈমান সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়: “কেউ ঈমান ত্যাগ করলে তার আমল নিষ্ফল হবে এবং সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে অর্ন্তভুক্ত হবে।” (৫:৫)
“তোমাদের মধ্যে কেউ যখন দ্বীন থকে ফিরে যায় এবং বেঈমান হয়ে মরে যায়, ইহকালে ও পরকালে তাদের আমল নিষ্ফল হয়ে যাবে। তারাই দোযখী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে।” (২:২১৭) কুফরের অর্থ সীমালংঘনও হয় যা পুরোপুরি ইসলামকে প্রত্যেখানের শামিল নয়, কিংবা আল্লাহ্-রাসূলের অস্বীকৃতিও বোঝায় না।
মনষী ইবনুল কাইয়েম কুফরকে ছোট ও বড় এই দু’ভাগে বিভক্ত করেছেন। বড় কুফরের শাস্তি স্থায়ী জাহান্নাম আর ছোট কুফরের শাস্তি জাহান্নমের অস্থায়ী বাস। একটি হাদীস লক্ষণীয় : “আমার উম্মাহর মধ্যে কুফরীর দু’টি (লক্ষণ) প্রচলিত আছে: “বংশ পরিচয় কলংকিত করা এবং মৃত্যে জন্য বিলাপ” এবং কেউ যদি গণকের খৌঁজ করে এবং তাকে বিশ্বাস করে তবে সে মুহাম্মদ (সা)-এর অবতীর্ণ ওহীর সাথে কুফরী করে।” হাদীসে আরো বলা হয়েছে: “(আমার পরে) পরস্পরকে হত্যা করে কুফরীর দিকে ফিরে যেয়ো না।” কুরআনের একটি আয়াতের এটা হচ্ছে ইবনে উমর (রা) ও অনান্য বিশিষ্ট সাহাবীর ব্যাখ্যা, আয়াতটি হচ্ছে: “আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তদনুসারে যারা বিধান দেয় না তারাই অবিশ্বাসী।” (৫:৪৪) আয়তটির বিভিন্ন ব্যাখ্যা আছে। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন: “এটা সেই কুফরী নয় যা একজনকে ইসলাম থেকে বহিষ্কৃত করে, বরং এটি হচ্ছে কুফরীর একটি উপাদান; কারণ যে ব্যক্তি এরূপ করে সে আল্লাহ ও কিয়ামত দিবসে অবিশ্বাস করে না।” তাউস একই অভিমত প্রকাশ করেছেন। আতা বলেন, এটা হচ্ছে কুফর অথবা অন্যায় অথবা ফিস্ ক যা অপরটির চেয়ে ছোট অথবা বড় হতে পারে। ইকরামার মতো অন্যরা যুক্তি দেখিয়েছেন: আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন সে অনুযায়ী যারা বিচার করে না তারা কুফরী করে। কিন্তু এই যুক্তিটা দুর্বল। কারণ এক ব্যক্তি শরীয়াহর আলোকে বিচার করুক আর নাই করুক, নিরেট অস্বীকৃতিই কুফর। এ প্রসঙ্গে ইবনুল কাইয়েম বলেন: আল্লাহ্র বিধানের পরিপন্থী বিচার বিবেচনার মধ্যে ছোট ও বড় দুই ধরনের কুফরী হয়ে থাকে। আর এটা নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গির ওপর। যদি সে বিশ্বাস করে যে, বিচার আল্লাহ্র বিধান অনুযায়ীই হতে হবে এবং শাস্তির সিদ্ধান্ত নিলো কিন্তু তা করা থেকে বিরত খাকলো তাহলে সে ছোট কুফরী করে। কিন্তু যদি কোন বিশ্বাসী মনে করে যে, এটা বাধ্যতামূলক নয় এবং ঈমানের পরিপন্থী যা খুশী তাই করতে পারে তাহলে সে বড় পাপ করে। কিন্তু যদি সে অজ্ঞতা ও অনিচ্ছাবশত ভুল করে বসে তবে তাকে কেবল “ভুল করেছে” এতটুকু বলা যাবে।
যা হোক বিষয়টির সারাংশ হচ্ছে, সকল সীমালংঘন ছোট কুফরের লক্ষণ, এই অর্থে অকৃতজ্ঞতা; কারণ মান্য করা বা আনুগত্যের মধ্যেই কৃতজ্ঞতার প্রকাশ। অতএব মানবীয় প্রচেষ্টা কৃতজ্ঞতা অথবা কুফর কিংবা এ দুয়ের মাঝখানে কোনো কিছু দিয়ে প্রকাশ পায়-প্রকৃত সত্য আল্লাহ্ পাকই জানেন।
শিরকও দু’ভাগে বিভক্ত: ছোট ও বড়। বড় শিরক হলো আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো উপাসনা করা অথবা তাঁর সাথে অন্য কাউকে শিরক করা। আল-কুরআনের একটি আয়াতে এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে: “আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরীক করলে তিনি মাফ করেন না। তিনি ক্ষমা করেন এর নিম্ন পর্যায়ের পাপ যাকে ইচ্ছা করেন।” (৪:৪৮)
ছোট শিরক হচ্ছে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে শপথ করা অথবা দুর্ভাগ্য সৌভাগ্য পরিণত করার জন্যে তাবিজ-তুমারের ক্ষমতায় বিশ্বাস করা। এই শিরক সম্পর্কে এক হাদীসে বলা হয়েছে, “যে আল্লাহ্ ছাড়া অপর কারো নামে শপথ করে সে শীরক করে এবং যে তাবিজ পরে সে শিরক করে।” (আহমাদ, আলহাকিম) এছাড়া “যাদু, তাবিজ ও ম্যাসকট (কোনো কিছু কে সৌভাগ্যের প্রতীক বলে মানা) বিশ্বাস হচ্ছে শিরক।” (ইবনে হাবান, আলহাকিম)
নিফাকও (মুনাফিকী) ছোট ও বড়-দু’ভাগে বিভক্ত। বড় মুনাফিকী হলো হৃদয়ে কুফরী পোষণ আর বাইরে প্রতারণার উদ্দেশ্যে ঈমানের ভাব করা। এ প্রসঙ্গে কুরআনে বলা হয়েছে: “মানুষের মধ্যে এমন লোক রয়েছে যারা বলে, আমরা আল্লাহ ও কিয়ামত দিবসে বিশ্বাস করি, কিন্তু তারা বিশ্বসী নয়।আল্লাহ্ ও ঈমানদারদের তারা ভাঁওতা দিতে চায়। তারা নিজেদের ছাড়া কাউকে প্রতারিত করে না এটা তারা বুঝতে পারে না।”(২:১৪)
এ ধরনের নিফাকের কথা সূরা আল-মুনাফিকুনে এবং কুরআনের অনান্য আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। এই নিফাকের জন্যে আল্লাহ জাহান্নামের শাস্তির ওয়াদা করেছেন।
“মুনাফিকরা তো দোযখের নিকৃষ্টতম স্তরে থাকবে এবং তাদের জন্যে তুমি কখনো কোনো সহায় পাবে না।” (৪:১৪৫)
ছোট নিফাকের লক্ষণ হচ্ছে আল্লাহ্ ও পরকালের প্রকৃতই বিশ্বাস আছে কিন্তু মুনাফিকের বৈশিষ্ট্যও আছে। ও ব্যাপারে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হাদীস হচ্ছে:
“মুনাফিকীর তিনটি লক্ষণ: সে যখন কথা বলে, (সর্বদা) মিথ্যা বলে; যখন সে প্রতিজ্ঞা করে (সর্বদা) ভঙ্গ করে; যদি তাকে বিশ্বাস করা হয় তবে (সর্বদা) সে অসাধু বলে প্রমাণিত হবে।” (অনুমোদিত হাদীস)
“যার মধ্যে (৪টি বৈশিষ্ট্য) আছে যে নির্ভেজাল মুনাফিক, যার মধ্যে একটি বৈশিষ্ট্য আছে তার মধ্যে নিকাফের একটি উপাদান আছে যতক্ষণ না সে একটি উপাদান আছে যতক্ষণ না সে এটা পরিত্যাগ করে: যখন সে কথা বলে, মিথ্যা বলে; বিশ্বাস করা হলে বিশ্বাসঘাতকতা করে; চুক্তি করা হলে খেলাফ করে এবং যদি সে ঝগড়া করে তবে খুব হঠকারী, অশালীন ও অপমানজনক আচরণ করে।”( অনুমোদিত হাদীস)
রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাহাবাগণ ও বুজুর্গানে দ্বীন এ ধরনের নিফাককে সবচেয়ে বেশি ভয় করতেন। তাঁরা বলতেন, এ ধরনের নিফাক নিফাক নিয়ে কেবল মুনাফিক ছাড়া আর কেউ নিশ্চিত বোধ করবে না, প্রকৃত ঈমানদারই কেবল যার ভয় করে।
৪. রূপকের ওপর গুরুত্ব প্রদান
বর্তমান ও অতীতে অনেক গোঁড়ামি ও ভুল বোঝাবুঝির মূল কারণ হলো স্পষ্ট ভাষণের প্রতি উপেক্ষা করে রূপক অর্থের ওপর বেশি গুরুত্ব দেয়া। রূপক আয়াত হচ্ছে যেগুলোর গূঢ় অর্থ আছে। আক্ষরিক অর্থই শেষ কথা নয়। আর সুস্পষ্ট আয়াত হচ্ছে পরিষ্কার স্বচ্ছ দ্ব্যর্থহীন যার অর্থ বুঝতে বেগ পেতে হয় না। কুরআনুল করীম বলছে: “তিনিই তোমার কাছে এই কিতাব পাঠিয়েছেন, যার কতক আয়াত সুস্পষ্ট দ্ব্যর্থহীন; এগুলো কিতাবের মূল অংশ আর অন্যগুলো রূপক। যাদের অন্তরে সত্য লংঘন প্রবণতা রয়েছে শুধু তারাই ফিত্ না এবং ভুল ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে যা রূপক তার অনুসরণ করে। আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেউ এর ব্যাখ্যা জানেন না।” (৩:৭)
প্রচীন বিদাতী ও গোঁড়া লোকেরা এই রূপক আয়াতগুলোকে চূরান্ত প্রমাণ বলে মনে করেছে। তারা স্পষ্ট মৌলিক বক্তব্যগুলোকে উপেক্ষা করেছে। বর্তমান চরমপন্থীরাও তাই করেছে। বিভিন্ন বিষয়ে তারা এর আলোকে সিদ্ধান্ত নিয়ে ভাল-মন্দ, শত্রু-মিত্র ও কাফির-ঈমানদার নির্ধারণ করেছে। ফলে এক মারাত্মক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। সতর্ক পর্যালোচনা ও পরীক্ষা- নিরীক্ষা ছাড়া কেবল রূপক আয়াতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেয়া জ্ঞানে অগভীরতা ছাড়া আর কিছু নয়। আল-খাওয়ারিজ এভাবে আত-তাকফিরের ফাঁদে পড়েছিলো। তারা তো সকাল মুসলমানকে কাফির বলে মনে করতো কেবল নিজেরা ছাড়া। ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়েই তারা হযরত আলীর (রা) বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল, অথচ তারা তাঁরই সহচর ও সৈনিক ছিলো। তাদের মত পাথর্ক্যের মূল কারণ ছিল আমীর মুয়াবিয়ার সাথে হযরত আলীর (রা) আপোস রফা। হযরত আলী (রা) সৈন্যদের সঙহতি ও মুসলমানদের জীবন রক্ষার জন্যে এ ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। কিন্তু আল-খাওয়ারিজ কুরআনের আয়াতের ভুল ব্যাখ্যা দিয়েআপোস অগ্রাহ করে। আয়াতটি হচ্ছে... “আল্লাহ ছাড়া কারো আদেশ দেয়ার ক্ষমতা নেই।” (১২:৪০০)
আলী (রা) তাঁর সেই বিখ্যাত উক্তি দিয়ে জবাব দিলেন, “একটি সত্য বাণী বাতিলের জন্যে ব্যবহৃত।” বস্তুত সকল আদেশ ও কর্তৃত্ব কেবল আল্লাহ্ র জন্যে- এর অর্থ এই নয়- মানুষ ছোটখাট ব্যপারে শরীয়াহর কাঠামোয় থেকে সিদ্ধান্ত নিতে পারবে না। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) আল-খাওয়ারিজের যুক্তি খন্ডন করেছেন। আপোস - সমঝোতা ইত্যাদি অনুমোদন করে কুরআনে যেসব আয়াত রয়েছে তিনি সেগুলোর উল্লেখ করেছেন। উদাহরণস্বরূপ স্বামী-স্ত্রীর সমঝোতা সংক্রান্ত আয়াতে বলা হয়েছে: “তাদের উভয়ের মধ্যে বিরোধ আশংকা করলে তোমরা তার পরিবার থেকে একজন ও স্ত্রীর পরিবার থেকে একজন সালিশ নিয়োগ করবে; তারা উভয়ে নিষ্পত্তি চাইলে আল্লাহ তাদের মধ্যে মীমাংসার অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করবেন।” (৪:৩৫)
কোনো হজ্জযাত্রী হজ্জের পোশাকে শিকার করলে সালিশরা তার ব্যাপারেও মীমাংসা করে দিতে পারে এমন দৃষ্টান্তও রয়েছে। কুরআন বলছে:
“হে মানদারগণ! ইহরামে থাকাকালে তোমরা শিকার জন্তু বধ করো না; তোমাদের মধ্যে কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে তা বধ করলে তার বিনিময় হলো অনুরূপ গৃহপালিত জন্তু যার ফয়সালা করবে তোমাদের মধ্যে দু’জন ন্যায়বান লোক-বিনিময়ের জন্তুটি কা’বায় পাঠাতে হবে কুরবানীরূপে অথবা তার কাফফারা হবে দরিদ্রকে খাওয়ানো কিংবা সমসংখ্যক সিয়াম পালন করা যাতে সে আপন কৃতকর্মের ফল ভোগ করতে পারে।” (৫:৯৫)
অতএব কুরআন ও সুন্নাহকে গভীরভাবে ও সতর্কতার সাথে অনুধাবন না করলে বিপথগামী হওয়ার আশংকাই সমধিক। বাড়াবাড়ি ও অগভীর জ্ঞানের ফাঁদে পড়ে আজকাল এক শ্রেণীর লোক খারিজীদের মতে শরীয়াহর তাৎপর্য সঠিকভাবে বোধগম্য না হওয়ার দুণই এরূপ গোঁড়ামির উদ্ভব হয়ে থাকে। অন্যদিকে গভীর জ্ঞানের অধিকারী লোক কখনোই হঠকরী আচরণ করতে পারে না। কুরআন-হাদীস সঠিক প্রেক্ষাপটে অধ্যয়ন করলে এর সুসংলগ্ন ও সুমহান অর্থ অনুবাধন করা অসম্ভব নয়। আর এর বিপরীত পন্থায় কুরআন পাঠের অর্থ হবে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ভাষায় তাদের মতো “যারা কুরআন তিলাওয়াত করে কিন্তু অর্থ তাদের হৃদয়ে স্পর্শ করে না।”
সম্ভবত এর মানে এই দাঁড়ায়- আল্লাহ ভাল জানেন- তাদের মৌখিক তিলাওয়াত শারীরিক কসরতের মতো যা কখনো হৃদয়কে প্রভাবিত করে না। এই কথাটি পূর্বে উদ্ধৃত “জ্ঞান ছিনিয়ে নেয়া” সংক্রন্ত হাদীসটির কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।
এ সংক্রান্ত ব্যাখ্যার সাথে হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর ব্যক্তব্যের সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয়। আবু উবায়েদের ফাযায়েলে কুরআন ও ইবরাহীম আত-তায়িমীর বর্ণনার ভিত্তিতে সাঈদ আবনে মনসুরের ব্যাখ্যায় এর উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি বলেন: “একদা একাকী বসে থাকার সময় উমর ইবনে খাত্তাব (রা) বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন, যারা এক রাসূলের অনুসরণ করে এবং কিবলার দিকে মুখ করে নামায পড়ে তারা কেন মতভেদে লিপ্ত হয়। উমর (রা) তখন ইবনে আব্বাস (রা)-কে গিয়ে জিজ্ঞেস করেন, “এই উম্মাহ কেন মতভেদে লিপ্ত হয় যখন তারা এক রাসূল (সা) ও এক কিবলাহ্র অনুসারী?” (সাঈদ-এর সাথে “এবং একই কিতাব” কথাটি যোগ করেছেন)। ইবনে আব্বাস (রা) জবাব দিলেন: “আল-কুরআন নাযিল হয়েছে এবং আমরা তা পাঠ করে ঐশী বাণীর মর্ম উপলব্ধি করেছি। কিন্তু এমন লোক আসবে যারা কুরাআন তিলাওয়াত করবে অথচ এর শানে নুযূল ও বক্তব্য বিষয় উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হবে। ফলে তারা বিভিন্ন রকম ব্যাখ্যা দেবে এবং মতানৈক্যে জড়িয়ে পড়বে।”
ইবনে আব্বাসের (রা)-এর জবানীতে সাঈদ আরো বলেন, “প্রতিটি গ্রুপের একটি মত থাকবে, তারপর মতবেদ থেকে সংঘাত সৃষ্টি হবে।” কিন্তু সেখানে উপস্থিত উমর ও আলী (রা) তাঁর এই অশুভ ব্যাখ্যা পছন্দ করলেন না এবং তাকে ভৎসনা করলেন। কিন্তু ইবনে আব্বাস (রা) চলে যাওয়া মাত্র তার মনে হলো যে, তার কথায় কিছু সত্য থাকতে পারে। তিনি তাকে ডেকে পাঠালেন এবং তার কথার পুনরাবৃত্তি করতে বললেন, সতর্ক বিবেচনার পর উমর (রা) ইবনে আব্বাস (রা)-এর সাথে একমত হলেন।
আশ-শাতিবী লিখেছেন: ইবনে আব্বাস (রা) সঠিক ছিলেন। যখন এক ব্যক্তি একটি সূরা নাযিলের কারণ জানে তখন সে এটাও বুঝতে পারে যে, এর ব্যাখ্যা ও উদ্দেশ্য কী। কিন্তু এ সম্পর্কে অজ্ঞতার ফলে তারা ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে মতভেদে লিপ্ত হয় এবং তাদের মতামতের পেছনে শারীয়াহর কোনো সমর্থন না থাকায় তারা বিভ্রান্ত হয়। এর একটি নযীর পাওয়া যায় ইবনে ওয়াহাবের বর্ণনায়: বাকির জিজ্ঞেস করলেন নাফিকে, “ইবনে উমর (রা) আল-হারুরিয়াদের সম্পর্কে কি চিন্তা করেন? (আল-খাওয়ারিজিকে আল-হারুরিয়াও বলা হয়। কারণ তারা হারাওয়া নামক একটি স্থানে দেখতে পান)। জবাব দিলেন, “ তিনি তাদেরকে খুব খারাপ লোক বলে মনে করেন। কুফফার সংক্রান্ত আয়াত তারা ঈমানদারদের ওপর প্রযোজ্য করে।” সাঈদ এই বক্তব্যের ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছেন, আল-খাওয়ারিজ যেসব রূপক আয়াতের অপব্যাখ্যা দেয় তাদের মধ্যে রয়েছে: “আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুসারে যারা বিধান দেয় না তারাই সত্য প্রত্যাখ্যানকারী।” (৫:৪৪) এর সাথে তারা জুড়ে দেয় এই আয়াতটি, তথাপি কাফেররা স্বীয় পালনকর্তার সংগে অন্যকে সমতুল্য করে। (৬:১)
সুতরাং তারা এই উপসংহার টানে যে, কোনো শাসক যদি ন্যায়পরায়ণতার সাথে শাসন না করে সে কুফরী করে। আর যে কুফরী করলো সে অন্যকে আল্লাহর সাথে শরীক করলো। অতএব সে শিরক করলো। আর এই ভুল বিচারের ভিত্তিতে তারা অন্যকে মুশরিকুন বলে ঘোষণা করে, তাদের সাথে যুদ্ধ করে এবং হত্যা করে। আবনে আব্বাস (রা) এই ধরনের অপব্যাখ্যা ও ভ্রান্ত ধারণার বারুদ্ধে হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেছিলেন। আর এর উৎপত্তি হয় ওহীর অর্থ বুঝতে অক্ষমতার দারুন।
নাফি বলেন, যখনি ইবনে উমর (রা)-কে আল-হারুরিয়াদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হতো তিনি বলতেন: “তারা মুসলমানদেরকে কুফফার ঘোষণা করে, তাদের রক্তপাত ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্তির অনুমোদন কের; তারা নারীর ইদ্দাহর সময় তাকে বিয়ে করে এবং স্বামীর বর্তমানে বিবাহিত মেয়েদের বিয়ে করে। আমি জানি না তাদের চেয়ে আর কে আছে যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যায়।” (শাতিবী, আলইতিসাম)
৫. বিশেষ জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা
চরমপন্থীদের জ্ঞানের অগভীরতার আরেকটি লক্ষণ হচ্ছে তারা ভিন্ন মতাবলম্বীর কথা শুনতে মোটেও রাজী থাকে না কিংবা কোনোরকম আলোচনায় বসতে চায় না। তাদের অর্থাৎ গোঁড়াদের মত যে অন্যের মতের আলোকে বিশ্লেষণ করে গ্রহণ বা বর্জন করা যেতে পারে তাও তারা স্বীকার করে না। তারা বিশেষজ্ঞ আলিমদের কাছ থেকে কোনো শিক্ষা পায়নি। বই-পুস্তক, সংবাদপত্র ইত্যাদি হচ্ছে তাদের স্বল্প জ্ঞানের একমাত্র উৎস। এগুলো আলোচনা পর্যালোচনার সুযোগও পায় না। ফলে তারা যা পড়ে তা থেকে ইচ্ছামতো সিদ্ধান্তে পৌঁছে। সুতরাং তাদের পড়া ও সিদ্ধান্তে যে ভুল হবে তাতে আর সন্দেহ কী! কেউ কোথাও কখনো তাদের মতো যুক্তিপূর্ণ সমালোচনা করলেও এগুলোর প্রতি কেউ তাদে দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। আশ-শারূয়াহ বুঝতে হলে যে নির্ভরযোগ্য আলিমদের শরণাপন্ন হওয়া উচিত সে প্রয়োজনীয়তাও তারা স্বীকার করে না।কোনো মুসলিম তরুণ যদি একা একা এরূপ প্রচেষ্টা চালায় তবে তা হবে আনাড়ি সাঁতারুর মতো গভীর পানিতে ঝাঁপ দেয়া।বিশেষজ্ঞদের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছাড়া শারীয়াহর জ্ঞান পূর্ণ হতে পারে না, বিশেষ করে সেসব ক্ষেত্রে যেগুলো নিয়ে মতভেদ আছে। এ কারণে আমাদের অভিজ্ঞ আলিমরা তাদের কাছ থেকে জ্ঞান আহরণের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেছেন যারা বিষয়বস্তু উপলব্ধি ছাড়াই কেবল কুরআনের হাফিজ হয়েছেন কিংবা কিছু বইপত্র পাঠ করে যাদের অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্কর হয়েছে।
এক শ্রেণীর এই তরুণদের বিভ্রান্তির জন্যে পেশাদার আলিম ও পন্ডিতরা বহুলাংশে দায়ী। তারা মনে করে এই আলিমরা শাসকগোষ্ঠীর সাথে হাত মিলিয়েছে। তাই তারা শাসকদের নির্যাতন, নিপীড়ন ও শরীয়ত বিরোধী কার্যকলাপের বিরোধীতা করার সাহস হারিয়ে ফেলেছে, বরং তারা মুনাফিকের মতো শাসকদের গর্হিত কাজের প্রশংসা ও সমর্থন করে। অথচ বাতিলকে সমর্থন না করে অন্তত তাদের নিশ্চুপ থাকাই নিরাপদ ছিল। সুতরাং তরুণরা বর্তমান এরূপ আলিমদের পরিবর্তে অতীতের আলিমদের অধিকতর নির্ভরযোগ্য মনে করলে অবাক হবার কিছু নেই। একাবর আমি তাদেরকে এ ব্যপারে জিজ্ঞেস করলে তারা পরিষ্কার বলেছে, “নির্ভরযোগ্য আলিম আমরা পাব কোথায়? যারা আছে তারা তো শাসকদের ক্রীড়নক। তাদের মর্জি-মাফিক ফতোয়াবাজীতে ব্যস্ত। শাসক যখন সমাজতন্ত্রী হয়, আলিমদের দৃষ্টিতে তাই ইসলামী; শাসক যদি হয় পুঁজিবাদী, পুঁজিবাদও তখন হয় ইসলামী! তাঁরা ফতোয়া দেন শত্রুর সাথে সন্ধি হারাম; কিন্তু শাসক যখন যুদ্ধ ঘোষণা করেন তখন তাদের জন্যে দোয়া করেন। “তারা আল্লাহ্ যা নিষিদ্ধ করেছেন তা হালাল করতে পারে।” (৯:৩৭)
এসব আলিম মসজিদ ও গীর্জা এবং মুসলিম পাকিস্তান ও হিন্দু ভারতকে সমান চোখে দেখে। আমি এর জবাব দিয়েছি এভাবে: “ব্যপারটি সাধারণ সত্যে পরিণত করা উচিত নয়। নিশ্চয় এমন আলিমও আছেন যারা বাতিলের নিন্দা করেন, নির্যাতন রুখে দাঁড়ান, একনায়কদের সাথে আপোস করেন না ভয়-ভীতি ও প্রলোভন সত্ত্বেও। এসব আলিমদের অনেককে কারাবরণ করতে হয়েছে। তারা নির্যাতিত হয়েছেন। এমনকি ইসলামের জন্যে শাহাদত বরণ করেছেন।”
সেই তরুণটি এটা স্বীকার করলেও বলল, “নেতৃত্ব ও ফতোয়া দেয়ার ক্ষমতা এখনো ঐ শাসকদের হাতে,
আলিমদের নয়-এরাই হচ্ছে তথাকখিত পথবিচ্যুত আলিম।”
অবশ্য এটা কেউ স্বীকার করতে পারেন না যে, ঐ যুবকটি যা বলেছে তা অনেকাংশে সত্য। নেতৃত্ব-অভিভাবকত্বের দায়িত্বপ্রাপ্ত এসব “প্রখ্যাত” “আলিম” সরকারের বন্ধকী পণ্যে পরিণত হয়েছেন এবং ইচ্ছে মতো ব্যবহৃত হচ্ছেন। এ ধরনের আলিমদের জানা উচিত সত্য সম্পর্কে নীরব থাকা বাতিল সমর্থনের শামিল। দুটোই শয়তানী কাজ। একবার মিসরীয় টেলিভিশনে “পরিবার পরিকল্পনা” ও “জন্মনিয়ন্ত্রন” অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণকারী একজন সুপরিচিত মুসলিম বুদ্ধিজীবী তো প্রশ্নই করে বসলেন, এই বিতর্কের উদ্দেশ্য কী, বিরোধীতা না সমর্থন-যাতে তিনি নিজের গা বাঁচিয়ে বক্তব্য রাখতে পারেন। বিতর্কের চেয়ারম্যান ঐ পণ্ডিতের প্রশ্ন শুনে আকাশ থেকে পড়লেন। অথচ এর আগের আলিমরা মত প্রকাশে নির্ভীক ছিলেন, কারো পরোয়া করতেন না। আল্লাহ্ এদের ওপর রহম করুন! এদেরই একজন মিসর সরকারের একজন প্রভাবশালী সদস্যকে সম্বোধন করে বলেছিলেন, “যে ব্যক্তি কাজের খোঁজে পা বাড়ায় তার ভিক্ষের হাত বাড়াবার দরকার পড়ে না।” সমসাময়িক আলিম বা পণ্ডিতরা এ থেকে শিক্ষা নিয়ে নিজেদেরকে নিঃসন্দেহে জ্ঞান-সমৃদ্ধ করতে পারেন।
এখন আলিমদের জ্ঞানগরিমা এতোই সঙ্কীর্ণ যে, তরুণ মুসলমানরা তাদের সংস্পর্শে এসে হতাশ হয়ে পড়ে। এ ধরনের একজন আলিম একবার একটি পত্রিকায় লিখলেন, পিতা ও পুত্রের লেনদেনে যেহেতু কোনো সুদের ব্যাপার থাকতে পারে না। কিন্তু পিতা ও পুত্রের তুলনা দিয়ে তিনি যে যুক্তি খাড়া করেছেন তা বিতর্কিত। মোটকথা এসব আলিম বিভিন্ন বিষয়ে সর্বসম্মত প্রামাণিক সূত্র বাদ দিয়ে দুর্বল সনদের হাদীস দিয়ে নিজেদের যুক্তি প্রতিষ্ঠিত করতে চান। এগুলো সাধুতা সত্যতার খেলাফ। মুসলিম তরুণরা স্বভাবতই এসব কাণ্ড কারখানা দেখে হতাশ হয়ে পড়ে। কোনো কোনো আলিম অনেক সময় সস্তা জনপ্রিয়তা অর্জিত হতে পারে এমন কাজও করে বসেন। এগুলো সচেতন তরুণদের নযর এড়াতে পারে না। আরেকটি ঘটনা।একবার মিশর সরকার বিভিন্ন ইসলামী গ্রুপের কার্যক্রম বন্ধ করে দিয়ে তাদের অনেক সদস্যকে বন্দী করেন। একজন সুখ্যাত আলিম প্রকাশ্য জনসভায় ঘোষণা দিলেন, ইসলামী গ্রুপকে আল্লাহ্ পরিত্যাগ করেছেন। তার যুক্তি ছিল, তাঁরা যদি সঠিক পথের অনুসারী হতেন তবে আল্লাহ্র রহমতে তাদেরকে পুলিশ বা সৈন্য কেউই পরাজিত করতে পারতো না। হক ও বাতিলের এরূপ অদ্ভুত বিচার সম্পূর্ণরূপে ইসলাম বিরোধী। ইসলামের দৃষ্টিতে সত্যের সংগ্রামীদের বিজয় লাভে কতকগুলো শর্ত আছে। সেই শর্ত পূরণ না হলে তাদের পরাজিত হওয়া অপ্রত্যাশিত নয়। অন্যদিকে পরিস্থিতির আনুকূল্যে বাতিলের বিজয় অর্জিত হলেও তা চিরস্থায়ী হতে পারে না, কিছুদিন টিকে থাকতে পারে মাত্র। সমকালীন ইতিহাসে এর অনেক জাজ্জল্যমান নযীর আছে। সবচেয়ে বড় কথা, এখন সত্য ও মিথ্যা বা হক বাতিলের দ্বারা জয়-পারজয় নির্ধারিত হয় না। জয়-পরাজয় নির্ধারিত হয় বৃহৎ শক্তিবর্গের হস্তক্ষেপ। আরবদের উপরে ইসরাঈলের ‘বিজয়’-এর একটি অত্যুজ্জ্বল নযীর।
আমরা কি জানি না, আতাতুর্ক ও তার দুষ্টচক্র মুসলমান জনগণ ও আলিমদের কী নির্মমভাবে দমন করেছে? খিলাফতের পাদপীঠ থেকে কিভাবে ইসলাম বিরোধী ধর্মনিরপেক্ষতা জবরদস্তি তুর্কী জনগণের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে! এখন বলুন, এ দু’পক্ষের মধ্যে কারা হক আর কারা বাতিল? সম্পতি একটি মুসলিম দেশে “পরিবার আইন” প্রবর্তনের বিরোধী বহু শ্রদ্ধাভাজন আলিমের উপর নির্যাতন চালানো এবং মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছে। অথচ ঐ পরিবার আইন সম্পূর্ণ ইসলাম বিরোধী। সংশ্লিষ্ট স্বেচ্ছাচারী সরকার সন্ত্রাসী কায়দায় ঐ আইনের বিরোধী জনসাধারণ ও আলিমকে স্তব্ধ করে দেয়। এর অর্থ কি এই যে, সরকারের পদক্ষেপ সঠিক ছিল, আর শাস্তিপ্রপ্ত আলিমরা ভ্রান্ত? আরেকটি মুসলিম দেশে অমুসলিম সংখ্যালঘু সংখ্যাগুরু মুসলমানদের উপর শাসন চালায়। সেখানে সরকার বিরোধী তৎপরতা দমনের জন্যে প্রায় প্রতিদিন হাজার হাজার মুসলমান নর-নারীকে গ্রেফতার করা হয় এবং নিপীড়ন চালানো হয়। তদুপরি যেসব দৃঢ়চেতা মুসলমান যুলুম সহ্য করে টিকে থাকে তাদের উপর হালাকু ও চেঙ্গিস খানের মতো হিংস্র কায়দায় নির্যাতন চালানো হয় আর তাদের সামনে তাদের কন্যা, বোন বা স্ত্রীদের ধর্ষণ করা হয়।
বস্তুত ইতিহাসে তথা ইসলামের ইতিহাসে মুসলমানদের ওপর এমন নির্যাতন, হত্যাযজ্ঞ ও ধ্বংসলীলার বহু নযীর আছে। হুসাইন ইবনে আলী (রা) পরাজিত হয়েছেন এবং ইয়াজিদ ইবনে আমীর মুয়াবিয়া তাঁর পবিত্র দেহকে ক্ষত-বিক্ষত করেছে। পরিণামে বনু উমাইয়া বহুকাল শাসন করেছে; কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বংশধাররা তাদের হাত থেকে নিষ্কৃত পাননি, এমনকি আব্বাসীয়দের শাসনামলেও নয়। এ থেকে কি এটাই প্রমাণিত হয় যে, ইয়াজিদের কার্যকলাপ সঠিক ছিল আর হযরত হুসাইন (রা)-এর অনুসৃত পন্থা বাতিল? হে আল্লাহ, আপনি এদের যুলুমের সাক্ষী, এদের হাত থেকে উম্মাহকে রক্ষা করুন!
আরো ঘটনা আছে। কয়েক বছর পর বিজ্ঞ ও সাহসী সেনাপতি আবদুল্লাহ ইবনে ইউসুফ অনারবী হাজ্জাজ-বিন-ইউসুফের হাতে পরা জিত হয়েছিলেন; পরে হাজ্জাজ আরেকজন মহান মুসলিম সেনাপতি আবদুর রহমান ইবনে আল-আসাস এবং সাঈদ ইবনে জুবায়ের, আশশাবী, মুতরিয়াসহ একদল বিশিষ্ট আলিমকে হত্যা করে। এগুলো ছিল উম্মাহর জন্যে বিরাট ক্ষতি, বিশেষ করে সাঈদ ইবনে জুবায়ের সম্পর্কে ইমাম আহমদ (র) বলেন, তিনি এমন এক সময় নিহত হলেন যখন তাঁর খুব প্রয়োজন ছিল। প্রসঙ্গত একটি ঘটনা উল্লেখ করা যায়: “আল্লাহর কসম! হিংস্র নেকড়ে যদি আমাদের ছিন্নভিন্ন করে তবুও আমরা আমাদের সত্য বিশ্বাস ও তোমাদের মিথ্যাবাদিতা সম্পর্কে সংশয়ী হবো না।” ইবনে জুবায়ের ও তার সঙ্গী-সাথীরা মক্কায় অবরুদ্ধ হয়ে বলেছিলেন: “আল্লাহর শপথ! সৎ মুত্তাকীদের কেউ অবনত করতে পারবে না যদি গোটা পৃথিবীও তাঁদের বিরুদ্ধে দাঁড়ায় আর বিপথগামীরা কখনোই যথার্থ সম্মান পাবে না যদি তাদের কপালে চন্দ্রও উদিত হয়। এসব উক্তি কুরআনে বর্ণিত নবীদের ঘটনাবলীর সাথে সংগতিপূর্ণ। কুরআন বলছে: “তবে কি যখনি কোনো রাসূল এমন কিছু এনেছে যা তোমাদের মনঃপূত নয় তখনই তোমরা অহংকার করেছে আর কতককে অস্বীকার করেছে এবং কতককে হত্যা করেছ!” (২:৮৭) এমন একজন নবীদের মধ্যে ছিলেন হযরত যাকারিয়া (আ) ও তাঁর পুত্র ইয়ারিয়া (আ)। এই নবীদের হত্যা এবং তাদের শত্রুদের সাফল্যকে কী পূর্বোক্তদের ভূমিকাকে মিথ্যা প্রমাণিত করে? আমরা কুরআনুল করীমে আসহাবুল উখদুদের ঘটনাও জানি। তারা ঈমানদারদের জলন্ত অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করে সেই বীভৎস্য দৃশ্য উপভোগ করতো: “এবং অন্য কোনো কারণে নয়, কেবল তারা সর্বশক্তিমান ও সকল প্রশংসার যোগ্য আল্লাহ্ কে বিশ্বাস করতো বলেই (কাফিররা) তাদের সাথে নিষ্ঠুর আচরণ করেছে।” (৮৫:৮)
কুরআন শরীফে বলা হয়েছে, ঈমানদারদের কখনো কখনো বিপদাপদের মধ্য দিয়ে পরীক্ষা করা হয় এবং বেঈমানদেরকে সাময়িক সাফল্য দিয়ে প্রলুব্ধ করা করা হয়। আল্লাহ বলেন: “মানুষ কি মনে করে আমরা ঈমান এনেছি এ কথা বললেই তাদেরকে পরীক্ষা না করে ছেড়ে দেয়া হবে? তাদের পূর্ববর্তীদেরও আমি পরীক্ষা করেছিলাম; আল্লাহ অবশ্যই প্রকাশ করে দেবেন কারা সত্যবাদী ও কারা মিথ্যাবাদী।” (২৯:২-৩)
ওহুদ যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয়ের পর নিম্মোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়: “যদি তোমাদের আঘাত লেগে থাকে তবে অনুরূপ আঘাত তাদেরও তো লেগেছে। মানুষের মধ্যে এই দিনগুলোর আমি পর্যায়ক্রমে আবর্তন ঘটাই, যাতে আল্লাহ মুমিনদেরকে জানতে পারেন এবং তোমাদের মধ্য থেকে কিছু লোককে শহীদ হিসেবে গ্রহণ করতে পারেন।” (৩:১৪০)
আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন, “...আমি তাদেরকে এমনভাবে ক্রমে ক্রমে ধরব, তারা তা বুঝতেও পারবে না।” (৬৮:৪৪)
৬. ইতিহাস, বাস্তবতা ও আল্লাহর সুনান সম্পর্কে সচেতনতার অভাব
ইসলাম সম্পর্কে সঠিক সচেনতার অভাব ছাড়াও বাস্তবতা, জীবন, ইতিহাস এবং আল্লাহ্ র সৃষ্টির রীতি সম্পর্কেও যথার্থ সচেনতার অভাব রয়েছে। এর অভাবে কিছু লোক অসাধ্য সাধন করতে চায়। যা ঘটতে পারে না তারা তাই কল্পনা করে এবং পরিস্থিতি ও ঘটনা প্রবাহের ভুল বিচার করে বসে যা আল্লাহ্ র রীতি ও শরীয়তী চেতনার পরিপন্থী। তারা অসমসাহসিক পদক্ষেপ নেয়, এমনকি জীবনেরও ঝুঁকি নেয়। এর পক্ষে বিপক্ষে কী প্রতিক্রিয়া হতে পারে তারা তা মোটেও বিবেচনা করে না। কারণ তারা মনে করে তাদের লক্ষ্য তো আল্লাহ্ ও তাঁর কালাম সমুন্নত করা। অতএব এসব লোকের পদক্ষেপকে অন্যরা “আত্মঘাতী” বা উম্মাদনাপূর্ণ বলে অভিহিত করলে আশ্চর্যের কিছু নেই।
বস্তুত এই মুসলমানরা যদি মুহুর্তের জন্যেও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সুন্নাহর প্রতি ভ্রুক্ষেপ করতো তাহলে নিশ্চিতভাবে সঠিক পথ-নিদের্শ লাভ করতো। আমরা এখানে স্মরণ করতে পারি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ১৩ বছরের মক্কী জীবন। তিনি শুধু দাওয়াত দিয়ে ক্ষান্ত হননি, ৩৬০টি মূর্তি থাকা সত্ত্বেও কা’বায় নামায ও তাওয়াফ করতে বলেছেন। কেন এরূপ করলেন? তিনি কাফিরদের তুলনায় তাঁর অনুল্লেখযোগ্য শক্তি ও অবস্থানের কথা ভেবে অতি বাস্তব পদক্ষেপ নিয়েছেন। তিনি কখনোই কমান্ডো হামলা চালিয়ে পাথরের মূর্তিগুলো ভেঙ্গে ফেলার চিন্তা করেননি। তাহলে তো আসর উদ্দেশ্যই পণ্ড হয়ে যেতো। ঐ পদক্ষেপে কাফিরদের মন থেকে তো বহু-ইশ্বরবাদের ভুত মুছে ফেলা যেতো না। তিনি সর্বাগ্রে চেয়েছিলেন তাঁর স্বজাতির মনকে মুক্ত করতে-কা’বাকে মূর্তিমুক্ত করতে নয়। এ জন্যে তওহীদেরশিক্ষা দিয়ে প্রথম মুশরিকদের মন পবিত্র করার লক্ষ্যে এমন একদল ঈমানদার তৈরি করেন যারা তাদের লক্ষ্য সম্পর্কে সচেতন এবং কঠোর অধ্যবসা ও পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে তারা বাতিলৈর বিরুদ্ধে হকের লড়াই চালিয়ে যেতে সক্ষম। এসব বিশ্বাসীর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তারা নিরলস নির্বিকার চিত্তে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্যে কাজ করে যায়, বিজয়ের উল্লাসে তারা মাদকতায় বিভোর হয়ে যায় না, আবার পরাজয়ে মুষড়ে পড়ে না। অবশ্য কখনো কখনো তারা কাফিরদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্যে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর অনুমতি প্রার্থনা করেছিল। কিন্তু তিনি এখনো সময় আসেনি বলে তা অগ্রাহ্য করেছিলেন এবং আল্লাহ্ র নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত ধৈর্য ধারনের উপদেশ দিয়েছিলেন। একদিন রাসূলুল্লাহ (সা) আম্মার বিন ইয়াসির (রা) ও তাঁর পিতাকে নিগৃহীত হতে দেখলেন। তিনি তাঁদেরকে সহ্য করার জন্যে উৎসাহিত করলেন এবং তাঁদের জান্নাতের সুসংবাদ দিলেন। স্বাধীনতা ও ধর্মরক্ষার জন্যে আল্লাহ্ র আদেশ না পাওয়া অবধি ঘটনা এভাবে চলতে থাকে। অবশেষে আদেশ এলো। কুরআনের ঘোষণা: “যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হলো তাদেরকে যারা আক্রান্ত হয়েছে। নিশ্চই আল্লাহ্ তাদেরকে সাহায্য করতে সক্ষম; তাদেরকে তাদের ঘরবাড়ি থেকে অন্যায়ভাবে উচ্ছেদ করা হয়েছে শুধু এ কারণে যে, তারা বলে: আমাদের প্রভু হচ্ছেন আল্লাহ্।” (২২:৩৯-৪০)
কিন্তু এই অনুমতি দেয়া হয়েছে কেবল তখনি যখন রাসূলুল্লাহ (সা) ও তাঁর সাহাবীরা নিজেস্ব আবাসভূমি স্থাপন করে নিজেদের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারপরই তাঁদেরকে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হয়েছৈ। তাঁরা এরপর একর পর এক বিজয় অর্জন করেছেন যতক্ষণ না তাঁরা আল্লাহ্ র হুকুমের মক্কা বিজয় করেছেন। এই মক্কা থেকেই তিনি চলে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন কাফিরদের অত্যাচারে।শৈষ পর্যন্ত তিনি মক্কার মূর্তি ধ্বংস করলেন এবং তিলাওয়াত করলেন এই আয়াত, “ বলো সত্র সমাগত এবং মিথ্যা বালুপ্ত হয়েছে। মিথ্যা তো বিলুপ্ত বাধ্য।” (১৭:৮১)
বিস্ময়ের ব্যাপার, জামায়াত আত-তাকফির আল-হিজরা ইতিহাসের এই ধারাকে অস্বীকার করে। এই অবাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে অবশ্য গ্রুপটির প্রতিষ্ঠাতা শেখ শুকরী ও আবদুর রহমান আবু আল-খায়েরের মধ্যে মতপার্থক্যও হয়েছিলো। আবু আল-খায়ের তাঁর “স্মৃতিকথায়” লিখেছেন যে, ইসলামের ইতিহিসের প্রতি শেখ শুকরীর অবস্থা ছিল না। তিনি এটাকে “অপ্রমাণিক ঘটনাবলী” বলে মনে করতেন। এটা ছিলো সাথে মতভেদের চতুর্থ বিষয়। তিনি কেবল কুরআন শরীফে বর্ণীত ঘটনাবলীকেই ইতহাসের উপাদান বলে মনে করতেন। তাই তানি ইসলামী খিলাফতের অধ্যায় পাঠ করা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন।
ধর্মীয় অজুহাতে ইতিহাস সম্পর্কে ও ধরনের সংকীর্ণ ও অযৌক্তিক দৃষ্টিভঙ্গির ফলে তারা ইসলামের ইতিহাসকেও হারাম ঘোষণা করেছিলেন। ইতিবাচক ও নেতিবাচক, জয় ও পরাজয় তথা সকল বিষয় সমন্বিত একটি জাতির ইতিহাস হচ্ছে সমৃদ্ধ খনির মতো যা থেকে সম্পদ আহরণ করে একটি জাতি তার বর্তমান গড়ে তোলে। যে জাতি ইতিহাসকে উপেক্ষা করে তার অবস্থা স্মৃতিভ্রংশ মানুষের সাথে তুলনীয়, যার কোনো মূল বা দিক-দর্শন নেই। কোনো গ্রুপ বা জনগোষ্ঠী কিভাবে এরূপ একটি অস্বাভাবিক শর্তকে টিকে থাকার ভিত্তি হিসেবে নির্ধারণ করতে পারে? তাছাড়া ইতাহাস হচ্ছে এমন একটি আয়না যাতে আল্লাহ্র বিধান প্রতিবিম্বিত হয়েছে। এজন্যে আর কুরআনে গোটা সৃষ্টিলোক সাধারণ ভাবে এবং মানব জীবনে বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। আর এ কারণেই আল কুরআন ইতিহাসের প্রেক্ষিত অনুধাবন এবং এ থেকে শিক্ষা গ্রহণের আহবান জানিয়েছে। এ প্রসঙ্গে কুরআনের বর্ণনা: “তোমাদের পূর্বে বহু জীবন প্রণালী গত হয়েছে, সুতরাং তোমরা দুনিয়া ভ্রমণ করো এবং দেখ মিথ্যাশ্রয়ীদের কি পরিণাম হয়েছে।” (৩:১৩৭)
আল্লাহ্ রীতির বৈশিষ্ট্য হলো স্থায়িত্ব, তার কখনো পরিবর্তন হয় না। আল কুরআন বলছে: “তারা আল্লাহ্ র নামে দৃঢ় অঙ্গীকার করে বলতে যে, তাদের কাছে কোনো সতর্ক বাণী এলে তারা অন্য সকল সম্প্রদায় অপেক্ষা সৎপথের অধিকতর অনুসারী হবে। কিন্তু যখন তাদের কাছে সতর্ক বাণী এলো তখন তা কেবল এদের বিমুখতাই বৃদ্ধি করলো, যমীনের বুকে ঔদ্ধত্য প্রকাশ এবং কূট-ষড়যন্ত্রের কারণে। কূট-ষড়যন্ত্র এর উদ্যোক্তাদেরকেই পরিবেষ্টন করে। তবে কি তারা প্রত্যক্ষ করেছে পূর্ববর্তীদের প্রতি প্রযুক্ত বিধানের? কিন্তু তুমি আল্লাহ্ র বিধানে কখনো কোন পরিবর্তন দেখতে পাবে না এবং আল্লাহর রীতিতে কোন ব্যাতিক্রম দেখবে না। (৩৫: ৪২-৪৩)
আল্লাহর রীতি যেহেতু অপরিবতর্নীয় ও স্থায়ী তাই যারা দুষ্কর্মে লিপ্ত হয় স্থান-কাল ও জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলের প্রতি আচরণে তিনি একই রীতি প্রয়োগ করেন। এই নীতির একটি শিক্ষনীয় দৃষ্টান্ত আমরা দেথেছি ওহুদের যুদ্ধে। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উপদেশ উপেক্ষা করার দরুন তাদেরকে কঠিন মূল্য দিতে হয়েছিলো। কুরআনুল করীমে একথা উল্লিখিত হয়েছৈ: “কী ব্যাপার! যখন তোমাদের ওপর মুসীবত এল তখন তোমরা বললে এটা কোথা থেকে এলো! অথচ তোমরা তো দ্বিগুণ বিপদ ঘটিয়েছিলে। বলো এটা তোমাদের নিজেদেরই নিকট থকে। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে শক্তিশালী। (৩:১৬৫)
আরেকটি আয়াতে যে কারণে মুসলমানদের পরাজয় বরণ করতে হয়েছে তার পরিষ্কার উল্লেখ করা হয়েছে: “আল্লাহ তোমাদের সাথে তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছিলেন যখন তোমরা আল্লাহ্ র অনুমতিক্রমে তাদেরকে বিনাশ করছিলে যে পর্যন্ত না তোমরা সাহস হারালে এবং নির্দেশ সম্বদ্ধে মতভেদ করলে এবং যা তোমরা ভালবাস তা তোমাদেরকর দেখবার পর তোমরা অবাধ্য হলে।” (৩:১৫২)
কিছু বিছিন্ন ঘটনার দরুণ ইতিহাসে অনেক সন্দেহজনক ঘটনা সংযোজিত হয় সত্য, কিন্তু মূল গটনা প্রবাহ সুরক্ষিত থাকে এবং একাধিক প্রামাণিক সূত্রে তা সমর্থিত হয়। আর সন্দেহপূর্ণ ঘটনাগুলো বিজ্ঞ ব্যাক্তি বিশ্লেষণ করতে পারেন। যাতে সত্য নিরূপণ করা যায়।
পক্ষান্তরে আমরা শুধু ইসলামের ইতিহাস নয়, সৃষ্টির পর থেকে মানব ইতিহাসের প্রতি আমাদের দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত করতে চাই। শুধু ঈমানদারদের ইতিহাস নয়, বরং নাস্তিকদের ইতিহাস থেকেও জ্ঞান আহরণ করা যায়। কেননা আল্লাহ্ র রীতিতে কোনো পক্ষপাতিত্ব নেই।তা তো তাওহীদ পন্থী ও পৌত্তলিক উভয়ের ক্ষেত্রেই সমভাবে প্রযোজ্য। বস্তুত জাহিলিয়ার ভ্রান্ত প্রকৃতি অনুধাবন করতে না পারলে আমরা কুরআনুল কারীমকে এবং ইসলামের বদৌলতে আমরা কী কল্যাণ লাভ করেছি তাও উপলব্ধি করতে সক্ষম হবো না। কুরআনে বলা হয়েছে: “...যদিও তারা পূর্বে স্পষ্ট বিভ্রন্তিতে নিমজ্জিত ছিলো।” (৩:১৬৪) এবং “তোমরা অগ্নি গহবরের কিনারে দাঁড়িয়েছিলে, আল্লাহ তা হতে তোমাদেরকে রক্ষা করেছেন।” (৩:১০৩)
উমর ইবনে খাত্তাব (রা)-এর একটি উক্তিতেও এই মর্ম প্রতিফলিত হয়েছে: “জাহিলিয়ার প্রকৃতি অনুধাবনে ব্যর্থতা শুরু হলে একে একে ইসলামের বন্ধনী বিছিন্ন হতে থাকবে।”
সত্য প্রকাশ যদি পুণ্য হয় তাহলে আমি বলবো ইসলামী আন্দোলনের সাথে সংশ্লিষ্ট অনেকেই ইতিহাস সঠিকভাবে অধ্যায়ন ও অনুধাবন করেননি। ইতিহাস পাঠের অর্থ শুধু বিশেষ বিশেষ সময়ের ঘটনাকে জানা নয়, বরং অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে এর মর্ম উপলব্ধি করা, শিক্ষা নেয়া এবং আল্লাহ্ র রীতিগুলো উদ্ভাসিত করা। নিছক পূর্ববর্তী জাতিগুলোর ধ্বংসাবশেষ অবলোকন করলে কোনো ফায়দা হবে না। শুধূ দেখা আর শোনার মাধ্যমে ইতিহাসের মর্ম উপলব্ধি করা যায় না। এ প্রসঙ্গে কুরআন বলছে: “তারা কি দেশে ভ্রমন করেনি? তাহলে তারা জ্ঞান বুদ্ধিসম্পন্ন হৃদয় ও শ্রুতিশক্তিসম্পন্ন কর্ণের অধিকারী হতে পারতো। আসলে চোখ তো অন্ধ নয়, বরং অন্ধ হচ্ছে বক্ষস্থিত হৃদয়।” (২২:৪৬)
ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর পুনরাবৃত্তি ঘটে এবং একটির সাথে অপরটির সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। কারণ এগুলো একই অপরিবর্তনীয় নিয়মে প্রবাহিত হয়। তাই পাম্চাত্য শিখিয়েছে: “ইতিহাসের চাকা ঘোরা” আর আরবারা বলে, “আজবকের রাত কালকের রাতের মতোই।”
আল কুরআনুল করীমে দৃষ্টিভঙ্গি ও আচার-আচরণে সাদৃশ্যের কারণ হিসেবে অভিন্ন চিন্তা ও দৃষ্টির উল্লেখ করা হয়েছে:
“যাদের জ্ঞান নেই তরা বলে, ‘আল্লাহ কেন আমাদের সাথে কথা বলেন না কিংবা কোন নিদর্শন আমাদের কাছে আসে না কেন? এর আগের লোকেরাও এ ধরনের কথা বলতো। তাদের হৃদয় একই রকম। আমি দৃঢ় প্রত্যয়শীলদের জন্য নিদর্শনাবলী স্পষ্টভাবে বিবৃত করেছি।” (২:১১৮)
কুরায়েশ পৌত্তলিকদের সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেছেন: “এভাবে এদের পূর্ববর্তীদের কাছে যখনি কোনো রাসূল (সা) এসেছেন তারা তাঁকে বলেছে, ‘তুমি তো এক যাদুকর, না হয় এক উম্মাদ!’ তারা কি একে অপরকে এই মন্ত্রাণাই দিয়ে এসেছে? বস্তুত তারা এক সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়।” (৫১:৫২-৫৩)
তাহলে দেখা যায়, আল্লাহ্ র নবীর প্রতি আগের ও পরের জাতিসমূহের দৃষ্টিভঙ্গির অভিন্নতা তাদের মধ্যে সমঝোতার ফলশ্রুতি নয়, বরং সাদৃশ্য হলো অন্যায় ও স্বচ্ছাচারী আচরণে। সুতরাং তাদের দৃষ্টভঙ্গি অভিন্ন কারণ হলো স্বেচ্ছাচারিতা।
যারা ইতিহাসের গুরুত্ব এবং আল্লাহর রীতির মর্ম উপলব্ধি করতে সক্ষম কেবল তারাই অতীত জাতিসমূহের ভ্রান্তি থেকে শিক্ষা নিতে পারে। তারাই প্রকৃত সুখী। তারাই যারা এসব ভুলভ্রান্তি থেকে নিজেরা সতর্ক হয় বটে, কিন্তু অন্যের ভাল দিকগুলোকেও উপেক্ষা করে না। জ্ঞানই ঈমানদারের লক্ষ্য তা সে যেখান থেকেই অর্জন করুক না কেনো। কেননা অন্য যে কোন ব্যাক্তির চেয়ে এটা তারই প্রাপ্য।
৭. দু’টি গুরুত্বপূর্ণ
সাধারণ মুসলমান, বিশেষত ইসলামী আন্দোলনের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যাক্তিদেরকে আল্লাহ্র দু’টি রীতি সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। প্রথম: সৃষ্টি ও বিধানের ক্ষেত্রে সুষ্পষ্ট পর্যায়ক্রমিকতা লক্ষণীয়। অথচ আল্লাহ্ পাক আঁখির পলক পড়ার চেয়ে কম সময়ের মধ্যে বেহেশত ও সৃষ্টিতে সক্ষম! “হও আর তা হয়ে যায়।” (২:১১৭)
তিনি তাঁর (হিসেবে) ছয় দিনে এগুলো সৃষ্টি করেছেন অথাৎ পর্যায়ক্রমে যা কেবল তিনিই জানেন। কেননা “দিন” সংক্রন্ত আমাদের ধারনা থেকে তা ভিন্ন। সকল প্রাণীর বিকাশের ক্ষেত্রেও পর্যায়ক্রমিকতা লক্ষণীয়। ধীরে ধীরে এগুলো পূর্ণতা লাভ করে। দাওয়াতী কাজেও এই প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হয়। পৌত্তলিকতা ও কুসংস্কার থেকে মনকে মুক্ত করার জন্যে প্রথমে সেখানে তওহীদের বীজ প্রোথিত করার প্রক্রিয়া শুরু হয়। এভাবে ঈমানের ভিত্তি মজবুত হলে ওয়াজিবাত ও মুহাররামাতের প্রক্রিয়া চালু করা হয়। এরপর সালাত, যাকাত, সিয়াম ইত্যাদি প্রবর্তন করা হয়। এজন্যে আমরা মক্কী ও মাদানী আয়াতের মধ্যে পার্থ্ক্য লক্ষ্য করি।
আয়েশা (রা) শারীয়ার প্রবর্তন এবং কুরআন নাযীলের পর্যায়ক্রম সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন: প্রথমে কুরআনের যেসব আয়াত নাযিল হয়েছে তাতে জান্নাত ও জাহান্নামের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। (পরে) যখন মানুষ ইসলাম গ্রহণ করলো তখন হালাল ও হারামের বিধান নাযীল হলৌ। যদি প্রথমেই “মদ পান করো না” এবং “ব্যভিচার করো না” নাযিল হতো লোকেরা বলতো, ‘আমরা মদপান ও ব্যভিচার কখনোই ছাড়তে পারব না।’ (বুখারী) সুতরাং যারা ইসলামী জীবন ব্যবস্থা তথা ইসলামী রাষ্ট্র প্রতাষ্ঠার সংগ্রামে নিয়োজিত তাদেরকে পরিবেশ, পরিস্থিতি, প্রতিবন্ধকতা, উপায়-উপকরণ ও সামর্থের দিকে লক্ষ্য রেখে পর্যায়ক্রমে দাওয়াতী কাজ চালাতে হবে। এক্ষেত্রে খলীফা উমর ইবনে আবদুল আজীজের দৃষ্টান্ত স্মর্তব্য। তিনি খেলাফায়ে রাশেদীনের আদর্শ জীবন পুনর্গঠন করেছিলেন। কিন্তু পুনর্গঠন প্রক্রিয়া সহজ ছিলো না। তার পুত্র আবদুল মালিক অত্যন্ত নিষ্ঠাবান মুসলমান ছিলেন। তিনি তাঁর পিতাকে একবার বললেন, “হে পিতা, আপনি কেন হত্যা করেন না? আল্লাহ্ শপথ, সত্যের জন্যে আমরা বা আপনার প্রাণ গেলেও আমি পরোয়া করি না।” কিন্তু উমর জবাব দিলেন, “তাড়াহুড়া করো না আমার পুত্র। আল্লাহ্ পাক কুরআনুল কারীমে দু’বার মদ্যপানেরনিন্দা করেছেন এবং তৃতীয়বারে নিষিদ্ধ করেছেন। আমার ভয় হয়, একবারেই সব চাপিয়ে দিলে এক সাথেই তা প্রত্যাখ্যাত হয় কিনা। এতে ফিতনার সৃষ্টি হতে পারে।” (আল মুয়াফাকাত)
দ্বিতীয়: দ্বিতীয় রীতিটি হচ্ছে প্রথমটির পরিপূরক। প্রতিটি জিনিসের পূর্ণতা বা পরিণতি লাভের নির্দিষ্ট মেয়াদ আছে। মূর্ত ও বিমূর্ত উভয় ক্ষেত্রেই এই রীতি প্রযোজ্য। ফসল পাকার আগেই কাটা যায় না। অপরিপক্ক ফলমূল ও শাকসবজি উপকারের পরিবর্তে ক্ষতি করতে পারে। ঠিক তেমনি মহৎ কাজের সুফল অনেক বছর পরেই পরিদৃশ্যমান হয়। পরিণত হতে যতো সময় লাগবে ততোই তা ফলপ্রদ হবে। এক পুরুষের চেষ্টা-সাধনা অন্য পুরুষে ফল দিতে পারে। মক্কা মুকাররমায় প্রথমদিকে কাফিররা আল্লাহর শাস্তির হুশিয়ারীকে অবিবেচকের মতো উপহাস করতো এবং দ্রুত শাস্তি আনার জন্যে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি আহবান জানাতো। কিন্তু তারা এটা জানতো না যে, নির্দিষ্ট সময়েই তা আসবে। বিলম্বও নয়, দ্রুতও নয়।
“তারা তোমাকে শাস্তি ত্বরান্বিত করতে বলে। যদি নির্ধরিত সময় না থাকতো তবে শাস্তি তাদের ওপর আসবে আকস্মিকভাবে, অজ্হতসারে।” (২৯:৫৩)
“তরা তোমাকে শাস্তি ত্বরান্বিত করতে বলে, অথচ আল্লাহ তাঁর প্রতিশ্রুতি কখনো ভঙ্গ করেন না, তোমাদের গণনার হাজার বছরের সামন।” (২২:৪৭)
এই পর্যায়ে আল্লাহ্ তায়ালা মহানবীর (সা)-এর প্রতি বিগত নবীদের মতো অধ্যবসায়ী হওয়ার উপদেশ দিলেন: “অতএব তুমি ধৈর্য ধারণ কর যেমন ধৈর্য ধারণ করেছিলেন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ রাসূলগণ।”(৪৬:৩৫) বিগত নবী-রাসূল ও তাঁদের অনুসারীদের কঠোর সঙগ্রাম ও ত্যাগ তিতিক্ষার বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন:
“তোমরা কি মনে করো তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে, যদিও এখনও তোমাদের কাছে তোমাদের পূর্ববর্তীদের অবস্থা আসেনি! অর্থ কষ্ট ও দুঃখ-ক্লেশ তাদেরকে স্পর্শ করেছিলো এবং তারা ভীত ও কম্পিত হয়েছিলো। এমনকি রাসূল এবং তাঁর ঈমানদার অনুসারীরা বলে উঠেছিলো, আল্লাহ্র সাহায্য কখন আসবে; নিশ্চয় আল্লাহ্র সাহায্য নিকটবর্তী। কিন্তু সেই নির্দিষ্ট সময় কেবল আল্লাহ্রই জানা আছে। এ জন্যে রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর সাহাবীদের ধৈর্য ধারণ করতে বলতেন এবং নিদির্ষ্ট সময়ের পূর্বে বিজয় প্রত্যাশা থেকে বিরত থাকতে উপদেশ দিতেন। একটি ঘটনা থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। একবার খারায ইবনে আল-আর্ত ইসলামের জন্যে তাঁর দুঃখকষ্ট বরণের কথা বলে আর্লাহ্ র সাহায্য প্রার্থনার আবেদন জানালে রাসূলুল্লাহ (সা) এতোই ক্রুদ্ধ হন যে, তাঁর মুখ লাল হয়ে যায়। তিনি বললেন: “তোমাদের আগে একজন বিশ্বাসীকে লোহা দিয়ে এমনভাবে পিষ্ট করা হয়েছে যে, হাড় ছাড়া তার শরীরের গোশ্ত ও শিরা-উপশিরা অবশিষ্ট ছিলো না। আর একজনকে করাত দিয়ে জীবন্ত অবস্থায় দু’ভাগে চিরে ফেলা হয়েছিলো। কিন্তু তাঁরা কেউই ধর্মত্যাগ করেননি। আল্লাহ্র শপথ, তিনি এমনভাবে দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করবেন যে, একজন ভ্রমনকারী সানা থেকে হাদ্রামাউত পর্যন্ত সফরের সময় এক আল্লাহ্ এবং তার ভেড়ার জন্যে নেকড়ে ছাড়া আর কাউকে ভয় করবে না। কিন্তু তোমরা অধৈর্য।” ( বুখারী)
৮. মুসলিম দেশ থেকে ইসলামের নির্বাসন
একজন নিষ্টাবান মুসলমানের কাছে বর্তমানে সবচেয়ে বেদনাদায়ক ব্যাপার হচ্ছে মুসলিম দেশগুলোতে এসলামী শিক্ষা অনুসারণের অভাবে বিকৃতি, দুর্নীতি ও মিথ্যা ব্যাপাকভাবে ছড়িয়ে পড়ছে। মার্ক্সবাদের ও ধর্মনিরপেক্ষতার ছোবলে মুসলিম সমাজ বিপর্যস্ত। আধুনিক “ক্রুসেডাররা” ক্লাব, থিয়েটার, অশ্লীলতা, পর্নোগ্রাফি, ছায়াছবি, নাচ-গান, মদ তথা সর্বক্ষেত্রে মুসলমানদেরকে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করছে। সংবাদপত্রে তারা অনুপ্রবেশের জাল বিস্তার করেছে। রাস্তাঘাটে অর্ধোলঙ্গ নেশাসক্ত নারীদের অবাধে চলাফেরা করতে দেখা যাচ্ছে। আর এসবই হচ্ছে মুসলিম সমাজকে অবক্ষয়ের দিকে ঠেলে দয়ার সুগভীর চক্রান্তের ফল।
এছাড়া মুসলিম দেশগুলোতে এমন সব বিষয়ে আইন প্রণয়ন করা হচ্ছে যা শরীয়তে নিষিদ্ধ অথচ ভাব দেখানো হয় উম্মার বিশ্বাস ও মূল্যবোধ উজ্জীবিত করাই এর লক্ষ্য। কিন্তু মূলত এসব আইনের উৎস শরীয়ত নয়,বরং ধর্মনিরপেক্ষ দর্শন। সুতরাং এতে বিস্ময়ের কিছু নেই- এসব আইন আল্লাহ্ যা নিষিদ্ধ করেছেন তাকে সিদ্ধ করে আর আল্লাহ্ যা সিদ্ধ করেছেন তাকে অসিদ্ধ ঘোষণা করে। আর এসব তথাকথিত আধুনিক আইন সব রকম দুর্নীতি ও অনাচারকে প্রশ্রয় দেয়। অন্যদিকে শাষকদের কার্যকলাপও হতাশাব্যঞ্জক। তারা ইসরামের শত্রুদের সাথে সন্ধি করে আর ইসলামের কথা শোনা যায় নিছক ধর্মীয় উপলক্ষ্য ছাড়া তাও আবার সাধারণ মানুষকে ধোঁধা দেয়ার জন্যে।
মুসলিম দেশগুলোর অর্থনৈতিক অবস্থা ও ব্যবস্থাপনা আরো করুণ। তরুণরা তাদের চোখের সামেন সামেন দেখেত পাচ্ছে ধনী ও দরিদ্রের কী অহসনীয় বৈষম্য! কেউ কোনোভাবে জীবন ধারণ করছে, এমনকি ওষুধপথ্যও সংগ্রহ করতে পারছে না কিংবা মাথা গোঁজারও ঠাঁই নেই। অন্যদিকে বিত্তবানরা লাখ লাখ টাকা মদ ও নারীর পেছনে ঢালছে, বড় বড় প্রাসাদে বাস করছে কিৎবা অনেক সময় খালিই পড়ে থাকে। বিদেশী ব্যাংকে তারা কোটি কোটি ডলার গোপনে সঞ্চয় করছে। তারা তেলের টাকা অপহরণ, পাশ্চাত্যের সাথে সহযোগিতা এবং আর্ন্তজাতিক কোম্পানীগুলোর সাথে লেনদেন করে বিত্তের পাহাড় গড়েছে। আর এই অর্থ তারা জুয়া এ নরীর পেছনে অকাতরে ব্যয় করছে। এর একটি অংশও যদি তারা দরিদ্র মানুষের জন্যে দান করতো তাহলে হাজার হাজার মানুষের অন্ন ও আশ্রয়ের সংস্থান হতো। অথচ এই সুবিধাভোগী শ্রেণী দিনে দুপুরে ডাকাতির মতো জনগণেরন সম্পত্তি অপহরণ করে চলছে। সুদ, ঘুষ, স্বজনপ্রীতি তো আছেই কিন্তু এদের বিরুদ্ধে আইন প্রয়োগ করার কেউ নেই। আইনের হাত থেকে বাঁচার রাস্তাও তাদের জন্য সহজ। সুতরাং এই নিদারুণ পরিস্থিতি সমাজের বিভিন্ন অংশের মধ্যে ঘৃণা-বিদ্বেষ সৃষ্টি করবে, এতে আর সন্দেহ কী! আর এই সুযোগের জন্যে ওৎ পেতে বেস থাকে সর্বনাশা মার্ক্সবাদীরা। তখন তারা বিকল্প হিসেবে শ্রেণী সংগ্রামের কাজ জারি করে দেয়।
এক্ষণে এই মর্মান্তিক অবস্থায় মূল কারণ সর্ম্পকে কোনো হেঁয়লির অবকাশ নেই। একটি পূর্ণাঙ্গ ভারসাম্যময় ও সুবিচারপূর্ণ বিধান হওয়া সত্ত্বেও ইসলাম আজ স্বদেশেই নির্বসিত। সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, রাষ্ট্র পরিচালনা, মানুষ ও সৃষ্টিকর্তার সম্পর্ক তথা সর্বক্ষেত্রে আজ ইসলাম অপসারিত। খ্রীষ্টানদের অবক্ষয়ের সময় যে অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিলো এখন মুসলমানদের অবস্থা তাই। ইসলামকে শরীয়ত ছাড়া দ্বীন, রাষ্ট্র ছাড়া ধর্ম এবং কর্তৃত্ব ছাড়া আইনের কিতাবে পর্যবসিত করা হয়েছে। মুসলমানদেরকে এমন পরিনামের দিকে ঠেলে দেয়া হয়েছে যার সাথে তার নিজস্ব ইতিহাসের কোনো সাদৃশ্য নেই। ক্যাথলিক গীর্জা সব রকম অনাচারে নিমজ্জিত হয়েছিলো। তারা স্বৈরাচারী শাসকদের পৃষ্টপোষকতা করে সাধারণ মানুষের ওপর নিপীড়ন চালিয়েছিলো। সামান্য বিরোধিতা তারা সহ্যকরতে পারতো না। স্বাধীনভাবে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা ছিলো নিষিদ্ধ। এ জন্যে তারা নিষ্ঠুর নির্যাতনের পথ বেছে নিয়েছিল। তারা বই পুড়িয়েছে, মানুষকেও পুড়িয়ে মেরেছে। সুতরাং এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ খুব স্বাভাবিক এবং ইউরোপে তাই হয়েছে। তারা গীর্জার জোয়াল থেকে এমনভাবেই নিজেদের মুক্ত করেছে যে, এখন গড্ডালিকা প্রবাহে ভেসে চলেছে আরেক ধ্বংসের দাকে। যা হোক, মুসলমানদেরকে কেন এই কালো ইতিহাসের পরিণাম ভোগ করতে হবে? ইসলাম কেন নির্বসিত হবে স্রেফ মসজিদে কিংবা মানুষের বিবকের সীমিত পরিসরে? কিন্তু মসজিদও আজ নিরাপদ নয়। সেখানেও জিহ্বাকে আংটাবদ্ধ রাখতে হয়। কেননা গুপ্ত পুলিশের কড়া নযর থাকে এগুলোর ওপর। মোটকথা মসজিদেও আজকাল ইসলামের বিপ্লবী ব্যাখ্যা দেয়ার অনুমতি নেই।
এই সমস্যার মৌলিক কারণ, মুসলমানদের ওপর চাপিয়ে দেয়া সেক্যুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষতা। ধর্মনিরপেক্ষতা ধর্মকে রাষ্ট্র, আইন প্রণয়ন ও ক্ষমতা থেকে বিচ্ছিন্ন রাখার শিক্ষা দেয়। মুসলিম উম্মাহর সামগ্রিক ইতিহাসে এরূপ অদ্ভুত শিক্ষার কোন নযীর নেই। কোননা আশ-শারীয়াহ শুধু ইবাদত-বন্দেগীর ভিত্তি নয়, বরং আইন, লেনদেন, ঐতিহ্য ও রীতি-নীতিরও উৎস। একথা সত্যি, কোনো কোনো মুসলমান শাসক সত্য পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছেন; কিন্তু অন্তত বিচার-আচারের ক্ষেত্রে শরীয়তকে উপেক্ষা করার তেমন নযীর নেই। এমনকি হাজ্জাজ বিন ইউসুফের মতো স্বেচ্ছাচারী শাসকও কুরআনুল কারীম ও সুন্নাহর ভিত্তিতে প্রদত্ত রায়কে অগ্রাহ্য করার ধৃষ্টতা দেখাতেন না। এই পার্থক্যটা অনুধাবনযোগ্য। ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি বা অবহেলার কারণে শরীয়ত থেকে বিচ্যুত হওয়া এক কথা আর আল্লাহর বিধান হিসেবে অন্যান্য মতবাদের সত্যতা ও শ্রেষ্ঠতা অস্বীকার করা ভিন্ন কথা। এদিকেই ইঙ্গিত দিয়ে আল্লাহ্ বলছেন: “নিশ্চিত বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য বিধান দানে আল্লাহ্ অপেক্ষা কে শ্রেষ্ঠতর?” (৫:৫০)
আরেকটি ব্যতিক্রমী বিষয় মুসলিম তরুণদের পীড়া দেয়। অমুসলিম দেশগুলো তাদেরই আদর্শ ও দর্শন মোতাবেক জীবন ধারা গড়ে তুলছে, অথচ কেবল মুসলমানরাই তাদের বিশ্বাস ও বাস্তবতা, তাদের দ্বীন ও সমাজের মধ্যে সৎঘাত জারি রেখেছে। আমার একটি বইয়ে লিখেছি: “ধর্মনিরপেক্ষতা খৃষ্টানরা গ্রহণ করতে পারে, কিন্তু তা মুসলমান সমাজে একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয়।” খৃষ্টধর্ম জীবনের জন্যে পূর্ণাঙ্গ ঐশি বিধান পেশ করতে পারে না যার প্রতি তার অনুসারীরা অঙ্গীকারবদ্ধ থাকতে পারে। খোদ বাইবেলে জীবনকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে: একটি ঈশ্বর অথাৎ ধর্ম অন্যটি সীজার অথাৎ রাষ্ট্র। এতে বলা হয়েছে: “সীজারের জন্যে নির্ধারিত বিষয় সীজারকেই চালাতে দাও আর ঈশ্বরের প্রাপ্য ঈশ্বরকে দাও।” (ম্যাথিউ-২২:২১)
সুতরাং একজন খ্রীষ্টান বিবেকের কোনরূপ দংশন ছাড়াই ধর্মনিরপেক্ষতা গ্রহণ করতে পারে। তাছাড়া তাদের পক্ষে ধর্মীয় শাসনের পরিবর্তে ধর্মনিরপেক্ষ শাসন গ্রহণ করার যুক্তি আছে। তাদের ধর্মীয় শাসনের অভিজ্ঞতা বড় নির্মম। অতীতে যাজকদের স্বেছ্ছাচারী শাসনের স্মৃতি তাদের মন থেকে মুছে ফেলা কঠিন। মুসলিম সমাজে ধর্মনিরপেক্ষতা মেনে নেয়া মানে আবাদত, বান্দেগী, আইন-কানুন, আচার-অনুষ্ঠান সবকিছুকে সর্বোতভাবে পরিত্যাগ করার শামিল। তাছাড়া বর্তমান যুগের চাহিদা পূরণে শারীয়াহ সক্ষম নয়- এই মিথ্যা দাবীর কাছে নতি স্বীকার করা। বস্তুত মানুষের রচিত আইন মেনে নেয়া মানে ঐশী বিধানের পরিবর্তে মানুষের সীমিত জ্ঞানকে শ্রেয় মনে করা, অথচ আল-কুরআন বলছে: “বল! তোমরা কি বেশি জান, না আল্লাহ্?” (২:১৪০)
এ কারণে মুসরমানদের কাছে ধর্মনিরপেক্ষতার দাওয়াত নাস্তিকতা ও ইসলাম পরিহারের দাওয়াতের সমতুল্য। শারীয়াহর পরিবর্তে একে শাসনের ভিত্তি বলে গ্রহণ করলে তা হবে সরাসরি রিদ্দাহ। এই বিচ্যুতি সম্পর্কে জনগণ নীরব থাকরে তা বড় ধরনের সীমালংঘন ও পরিষ্কার অব্াধ্যতার নযীর বলে গণ্য হবে। এর ফলে মুসলিম সমাজে অপরাধবোধ, দীনতা, হিংসা, ঘৃণা ও ক্ষোভ সৃষ্টি হতে বাধ্য। বস্তুত ধর্মনিরপেক্ষতা মূলত ঈশ্বর সম্পর্কে তাদের নিজেস্ব ধ্যান-ধারণাই ফসল। এই মতবাদের দৃষ্টিতে ঈশ্বর জগত সৃষ্টি করেছেন বটে, কিন্তু এর দেখাশোনার দায়িত্ব ত্যাগ করেছেন অথাৎ জগতের সাথে ঈশ্বরের সম্পর্কে ঘড়ির সাথে ঘড়ি-নির্মাতার সম্পর্কের মতো। ঘড়ি-নির্মাতা ঘড়ি তৈরি করে দেয়ার পর নির্মাতার সাহায্য ছাড়াই চলতে পারে, তেমনি আল্লাহ পৃথিবী নির্মাণের পর তা আপন গতিতেই চলছে। এই ধারণা এসেছে গ্রীক দর্শন থেকে। এরিস্টলের মতে আল্লাহ পৃথিবী নিয়ন্ত্রন করেন না এবং এ সম্পর্কে কিছুই খবর রাখেন না। উইল ডুরান্ট এক ধাপ এগিয়ে তাকে বলেছেন অসহায় ঈশ্বর। সুতরাং এতে আর আশ্চর্যের কী আছে, যে ঈশ্বর তার সৃষ্ট জীবের খবরই রাখেন না তিনি কী করে তাদের জীবন যাত্রার বিধান তৈরি করবেন? এ দায়িত্ব ছেড়ে দেয়া ছাড়া তো তার গত্যন্তর নেই! ইসলামের ধারনা থেকে এই ধারণা সম্পূর্ণ বিপরীত। আমরা মুসলমানরা বিশ্বাস করি আল্লাহ্ একই সাথে জগতের সৃষ্টিকর্তা, বিধানদাতা ও পালনকর্তা : “... তিনি সবকিছুর বিস্তারিত হিসাব রাখেন।” (৭২:২৮)
তিনি সর্বশক্তিমান ও সর্বদর্শী; তাঁর দয়া ও বদান্যতা সকলের জন্য যথেষ।ট। এই ক্ষমতা বলেই তিনি মানুষের ঐশী পথ রচনা করছেন, হালাল-হারাম নির্ধারণ করে দিয়েছেন এবং বান্দাদেরকে তাঁরই বিধান মেনে চলতে এবং সেই অনুযায়ী ফায়সালা করার নির্দেশ দিয়েছেন। যদি তারা না করে তবে তা হবে কুফরী ও সীমালংঘন।
নিষ্ঠাবান মুসলিম তরুণরা এ ধরনের অনাচার তাদের চোখের সামনেই দেখেছে কিন্তু কিংকর্তব্যবিমূঢ়। তারা শক্তি প্রয়োগ কিংবা গলাবাজি করে এ সবের পরিবর্তন করতে পারছে না। তাদের একমাত্র উপায় মনের মণিকোঠায় গভীর অনুভূতি পোষণ যা ঈমানের দুর্বলতম অঙ্গ। অবশ্য, এই হৃদয়াবেগ চিরদিন চাপা থাকবে না। একদিন না একদিন তার বিস্ফোরণ ঘটবেই।
এছাড়া ইসলামী বিশ্ব ও মুসলমানদের পবিত্র স্থানসমূহ সর্বগ্রাসী হামলার শিকার। ইহুদীবাদ, খৃষ্টবাদ, পৌত্তলিক, মার্ক্সবাদী তথা সকল ইসলাম বিরোধী শক্তি তাদের মত পার্থক্য ভুলে একযোগে প্রকাশ্যে অথবা গোপনে ইসলামী পুনরুজ্জীবন, ইসলামী আন্দোলন অথবা ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে হীন তৎপরতা চালিয়ে যাছ্ছে। এ কারণে সকল অনৈসলামী ইস্যু প্রাচ্য ও প্রতীচ্য, বিশেষত আমেরিকা ও রাশিয়ার নৈতিক ও বৈষয়িক মদদ পায়, কিন্তু ইসলামী ইস্যুতে তারা নির্বিকার। আল্লাহ তায়ালা কুরআন মজীদ বলছেন: “বেঈমনারা একে অন্যের সমর্থক।” (৮:৭৩)
কিন্তু ভাষা-বর্ণ-গোত্র-স্থান-কাল-নির্বিশেষে মুসলমানরা অন্য মুসলমানের বিপদাপদে, নিগ্রহ নিষ্পোষণ ও হত্যাযজ্ঞে নীরব থাকতে পারে না। কারণ তারা সেই সবূত্তোম উম্মাহর অন্তর্ভুক্ত যারা একই ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ। কেননা যে মুসলমানের মনে অন্য মুসলমানের সম্পর্কে কোনো অনুভূতি নেই, সে মুসলমান নয়।
প্রতিদিন খবর আসছে ফিলিস্তিন, লেবানন, আফগানিস্থান, ফিলিপাইন, ইরিত্রিয়া, সোমালিয়া, সাইপ্রাস ও ভারতে মুসলমানরা কিভাবে নিগৃহীত হচ্ছে। অথচ আমরা দেখি আজকাল অন্য কোনো মুসলিম দেশ এ ব্যাপারে কোনো উচ্চবাচ্য করে না, বরং সম্পূর্ণ উদাসীন। আরো মর্মান্তিক, কোনো কোনো শাসক ইসলামের শত্রুদের সাথে গাঁটছড়া বাঁধেন। তারা স্রেফ গোত্রীয়, আঞ্চলিক বা জাতিগত স্বার্থ রক্ষায় ব্যস্ত।
আল্লাহ, তাঁর রাসূল, দ্বীন, উম্মাহ ও এর স্বার্থের প্রতি তাদের কোনো আনুগত্য বা অনুভূতি নেই। তরুণরা আরো লক্ষ্য করছে, ইসলামের প্রতি শাসকদের এই নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির নেপথ্যে কাজ করছে ইহুদী, খ্রীষ্টান ও কম্যুনিজমের চক্রান্ত। কিন্তু শাসকদের মনে ভীতি সৃষ্টিকরে এবং তাদেরকে ইসলামী আন্দোলনদমনে প্ররোচিত করে।
বহুবিধ বিষয়ের মধ্যে আরেকটি বিষয় বিগত কয়েক বছরে মুসলিম তরুণদের মদ্যে হতাশা সৃষ্টি করেছে। এটি হচ্ছে ১৯৬৭ সালের ৬ দিনব্যাপী মিসর-ইসরাঈল যুদ্ধ। এই যুদ্ধের মারাত্মক প্রতিক্রিয়া রোধের লক্ষ্যে যুদ্ধের জন্য দায়ি ব্যক্তিরা এই আশ্বাস বাণী শোনালেন যে, এটা “পূর্বাবস্থায় প্রত্যাবর্তন”- তেমন ক্ষতিকর কিছু নয়। অথচ আরব দেশগুলোর তরুণরা শৈশব থেকে এই অঞ্চলে চালিয়ে দেয়া হয়েছে এবং এই এলাকাকে মুক্ত করা মুসলমানদের ধর্মীয় ও জাতীয় দায়িত্ব। ফিলিস্তিনের গ্রান্ড মুফতী মরহুম আমীন আল-হুসয়নী (র) -এ ব্যাপারে বলেছিলেন, “ফিলিস্তিন জনবসতিহীন জনপদ নয় যে, এখানে জনপদহীন লোকদের আশ্রয় দিতে হবে।” যা হোক ১৯৬৭ সালের যুদ্ধে শোচনীয় পরাজয়ের পর পরিস্থিত নতুন মোড় নিলো অথাৎ আগ্রাসনের ক্ষতি কাটিয়ে ওঠার নামে ইসরাঈলকে স্বীকৃতি দেয়ার মতো পরিস্থিতি সৃষ্টির কৌশল অবলম্বন কর হলো। এর অর্থ দাঁড়ায়, সাম্প্রতিক ইসরাঈলী আগ্রাসনে পুরানো আগ্রাসনকে বৈধ বলে স্বীকার করে নেয়া হয়। যদি তাই হয়, তাহলে ১৯৪৯, ১৯৫৬ ও ১৯৬৭ সালের যুদ্ধের কী কারণ ছিল? গোড়াতেই ইসরাঈলকে স্বীকৃতি দিলে মুসলিম উম্মাহ মারাত্মক পরিণতির হাত থেকে রেহাই পেতো। বস্তুত তথাকথিত “শান্তিপূর্ণ সমাধান” ও শান্তিচুক্তির অজুহাতে এসব অবমাননাকর উদ্যোগ নেয়া হয়। ক্ষমতাসীন কর্তৃপক্ষ সামরিক, রাজনৈতিক, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিকে সামনে রেখে তাদের নীতির পক্ষে সাফাই দেন। কিন্তু এসবই মুসলমানদের আশা-আকাংখায় তীব্র আঘাত হানে, বিশেষ কর ইসরাঈলের প্রতি সকর বৃহৎ শক্তির স্বীকৃতি ও সমর্থন এবং মুসলিম স্বার্থের প্রতি উপেক্ষা মুসলমানেদের আঘাত তীব্রতর করে। এসব ঘটনা থেকে এই উপসংহার টানা যায় যে, ইসলামের বিরুদ্ধে নতুন করে ক্রুসেড শুরু করা হচ্ছে। এসরামী বিশ্ব ও ইসরামী আন্দোলনের প্রতি পাশ্চাত্য ও পাশ্চাত্যের রাজনৈতিক নেতাদের মনোভাবে এটা পরিস্ফুটিত। মুসলমানদের সাথে শতাব্দী প্রাচীন লজ্জাকর লড়াইয়ের স্মৃতি তাদের মনে এখন তরতাজা রয়েছে। তাই তাদের অন্তরে এখনো মুসরিম বুদ্ধিজীবি অবশ্য এই ধারণা বাতিল করে যুক্তি দেখাতে চান যে, পাশ্চাত্যে ক্রুসেড চেতনা নয়, তাদের জাতীয় স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখেই সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু সাম্প্রতিক পরিস্তিতি তাদের এই দাবীকে ভুল প্রমাণিত করেছে, বরং পাশ্চাত্যে ক্রুসেড চেতনা পূর্ণমাত্রায় জীবন্ত। আমি আমি এলেনবী অথবা জেনারেল গুরান্ডের কথা বলতে চাই না। আমাদের সমসাময়িকদের মনেই প্রশ্ন জেগেছে : কেন পাশ্চাত্য মুসলিম ভূখন্ডে ইসরাঈলের অস্তিত্ব বহাল রাখতে আগ্রহী? কেন যুক্তরাষ্ট্র ইসরাঈলের নিন্দা সম্বলিত প্রতিটি জাতিসংঘ প্রস্তাবে ভেটো দেয়? কেন তারা ইরিত্রিয়ার বিরুদ্ধে মার্ক্সবাদী ইথিওপিয়াকে সমর্থন যোগায়? কেন সংবাদপত্রে মুসলিম দেশের ঘটনাবলী গুরুত্ব সহকারে স্থান পায় না? অথচ বিশ্বের কোথাও একটি বিমান হাইজ্যাক হলে যেন তুলকালাম কান্ড শুরু হয়? কেন তারা অন্যদের চেয়ে আরবদের সস্তা মনে করে? আসলে এগুলোর কোনো ব্যাখ্যা নেই। প্রকৃতপক্ষে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ইহুদীবাদ, খৃষ্টবাদ ও কম্যুনিজমের শয়তানী আঁতাত গড়ে উঠেছে।
বস্তুত মুসলিম তরুণদের মতে মুসলিম দেশগুলোর শাসকরা বিদেশী শক্তির দাবার গুটিমাত্র। তাদেরকে সামরিক অভ্যুথ্থানের মাধ্যমে ক্ষমতায় এনে মুসলমানদের চৌখে ‘হীরো’ সাজানো হয়। এই ধারণার মধ্যে অতিশয়োক্তি থাকলে থাকতে পারে, কিন্তু সামগ্রিক ঘটনা প্রবাহের আলোকে একেবারেই ভিত্তিহীন নয়। এসব ঘটনা চোখে আয়্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় যে, ইসলামী পুনর্জাগরণ অঙ্কুরে বিনষ্ট করার জন্যেই এই শাসকরা শয়তানী চক্রের ফাঁদে পা দিয়েছে। এই নেতারা দৃশ্যত মুসলমান ও ইসলামের জন্যে কুম্ভীরাশ্রু বর্ষণ করে, আসলে তারা মুসলিম উম্মাহর শত্রুদের পোষা এজেন্ট।
৯. ইসলামী দাওয়াতে প্রতিবন্ধকতা
আরেকটি বিষয়ের দিকে আমাদের দৃষ্টি দেয়া দরকার। বিষয়টি হচ্ছে ইসলাম প্রচারে স্বাধীনতা। ইসলাম শুধু নিজেকে সৎ হিসেবে গড়ে তোলার শিক্ষা দেয় না, অন্যকেও সংশোধনের তাগিদ দেয়। মানুষকে ভাল কাজের আদেশ দেয় ও খারাপ কাজ থেকে বিরত প্রচেষ্টাকে এ কারণে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। তাই প্রত্যেক মুসলমানকে তার সামর্থ অনুযায়ী ইসলাম প্রচারের কাজে অংশ নিতে হবে। এ জন্যে কুরআনে বলা হয়েছে: “তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের পথে আহবান করো।”...(১৬: ১২৫)
রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রত্যেক সাহাবী ছিলেন ইসলাম প্রচারক (দাইয়া)। কুরআন আরো বলছে: “বল, এটাই আমার পথ: আল্লfহর প্রতি মানুষকে আমি আহবান করি সজ্ঞানে। আমি ও আমার অনুসারীগণ।” (১২:১০৮)
অতএবসংস্কার কর্মীদের লক্ষ্য হচ্ছে: “নিজে সৎ হও অপরকে সৎ করো।” আলকুরআনের ভাষায়: “কে উত্তম আল্লাহ্র (সাহায্যের) হাত জামা’তের সাথেই থাকে।” তিনি আরো বলেন: “একজন ঈমানদার আরেকজন ঈমানদারের কাছে সেই ইমারতের মতো যার বিভিন্ন অংশ একে অপরের সাথে সংযুক্ত।” (বুখারী)
নিজেদের মধ্যে সহৃদয় সহযোগিতা এবং সৎ কাজের আদেশ কেবল একটি ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা নয়, বরং একটি অপরিহার্য শর্ত। অতএব দাওয়াতী ক।ষেত্রে সামষ্টিক কাজ বাধ্যতামূলক- এছাড়া দায়িত্ব অপূর্ণ থাকে। বাস্তব কথা হচ্ছে ইসলাম বিরোধী শক্তি বিভিন্নভাবে সংগঠনের মাধ্যমে কাজ করছে, অতএব মুসলমানদেরকেও সংঘবদ্ধ হয়েই ঐ শক্তির মোকাবিলা করতে হবে। আন্যথায় আমরা পিছিয়ে পড়তে থাকব যখন অন্যরা এগুতে থাকবে। অতএব যেসব মুসলিম দেশে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে পরিচালিত দাওয়াতী কাজের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হয়, সরকারীভাবে এমনকি সেন্সরশীপের মাধ্যমে তারা মস্ত বড় গুনাহ করে। দাওয়াতী কাজে ভীতি প্রদান ও বাধা সৃষ্টিও চরমপন্থী মনোভাব সৃষ্টির প্রধান কারণ, বিশেষ করে যখন ধর্মনিরপেক্ষতা ও মার্ক্সবাদ প্রচারে কোনো বাধা দেয়া হয় না; বরং সকর সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়া হয় তখন এটাকে কিছুতেই সহজভাবে মেনে নেয়া যায় না। এটা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক এ কারণে যে, মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে ইসলামী বিপ্লবের কাজে বাধা দেয়ার অধিকার কারো নেই, কোনো সরকারেরও থাকতে পারে না।
বস্তুত মুসলিম দেশগুলোতেই ইসলামকে পরিপূর্ণ জীবন বিধান হিসেবে প্রতিষ্ঠার চেষ্ঠা করতে গিয়ে সেন্সরশীপ ও নানা রকম দলনের শিকার হতে হচ্ছে। সেখানে ইসলামের চেহারা হচ্ছে পশ্চাদপদতা ও অবজ্ঞায় এবং আচার-অনুষ্ঠান, বিদাতী কাজ কাম, শাসক-তোষণ এবং শাসকদের গদী বহাল রাখার দেয়ার মধ্যে সীমিত। আর দুর্নীতিপয়ারণ শাসকরাও এ ধরনের ইসলামের পৃষ্ঠপোষকতায় অতি উৎসাহী। এভাবে অন্যায়-অবিচার শোষণ-নির্যাতনের বিরুদ্ধে জিহাদকে তারা স্যাবোটাজ করার অপচেষ্টা চালায়। মার্কস সম্ভবত এই অর্থে দাবী করেছিলেন, “ধর্ম জনগণের জন্যে আফিম।”
কিন্তু কুরআনুল করীম, সাহাবায়ে কিরাম, তাবিঈন যে ইসলাম রেখে গেছেন তা হচ্ছে সত্য, শক্তি, সম্মানান-মর্যাদা, ত্যাগ-তিতিক্ষা ও জিহাদের প্রতিভূ। আর শাসকরা এই ইসলামকে ভয় পায়; কারণ তাদের অনাচার-অবিচারের বিরুদ্ধে কি জানি কখন বিদ্রোহ দেখা দেয়! পক্ষান্তরে এই ইসলাম তার অনুসারীদেরকে বলে: “তারা আল্লাহর বাণী প্রচার করতো এবং তাঁকে ভয় করতো, আর আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করতো না।” (৩৩:৩৯)
এই পরিছন্ন বিশ্বাসের আলোকে ঈমানদাররা মনে করে যেহেতু জীবন মেয়াদ আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত, অতএব কাউকে ভয় করার দরকার নেই, আর তিনি ছাড়া কারো কাছে পার্থনারও দরকার নেই। সমসাময়িক তুরস্কের একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। একবার একজন উপপ্রধান মন্ত্রীকে মন্ত্রণালয় থেকে কারাগারে নিয়ে যাওয়া হয়। তিনি একটি দলের নেতা। তাদের বিরুদ্ধে শরীয়ত প্রবর্তন করার দাবী জানানোর অভিযোগ আনা হয়। অথচ তুরস্কের ৯০ ভাগ মানুষ মুসলমান! উক্ত নেতা ও তার অনুসারীদের বিরুদ্ধে ১৫টি অভিযোগ খাড়া করা হয়। অভিযোগগুলোর মূল বিষয় ছিলো তারা ধর্মনিরপেক্ষ তুরস্ককে এসলামী রাষ্ট্রে পরিণত করতে চান। ধর্মনিরপেক্ষ আতাতুর্কের অনুসারী তুরস্কের তদানীন্তন সামরিক সরকার শরীয়ত তথা আসলামী জীবন বিধান পুনঃপ্রবর্তনের যে কোন প্রচেষ্টাকে অপরাধ বলে গণ্য করে। অথচ উক্ত গ্রুপ সর্বসম্মত আইনানুগ পন্থায় গণতান্ত্রিক পরিবেশে তাদের কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। তারা শক্তি প্রয়োগ করে সহিংস পন্থায় সরকার উৎখাত করতে চাননি। সামরিক কৌশুলী তাদের বিরুদ্ধে নানা আপত্তিকর শ্লোগান তোলার অভিযোগও উথ্থাপন করে। শ্লোগানগুলো ‘আশাশারীয়াহ এবং ইসলাম এক ও অভিন্ন’ এবং আল-কুরআনই হচ্ছে সংবিধান।’
প্রশ্ন হচ্ছে, কোনো মুসলমানই যিনি আল্লাহকে প্রভু, ইসলামকে দ্বীন ও হযরত মুহাম্মদ (সা) কে রাসূল হিসেবে স্বীকার করেন তার পক্ষে কী এগুলো অস্বীকার করা সম্ভব? যখন ঈমানের পরিবর্তে কুফর এবং হারামকে হালাল করা হয় তখন মুসলমানদের কীকরা উচিত? এসব অস্বাভাবিক পরিস্থিতি কী বাড়াবাড়ি ও চরমপন্থার মূল কারণ নয়? একটি আফ্রো-আবর দেশে কম্যুনিস্ট তৎপরতার জন্যে সাংবিধানিক সুযোগ ও নিরাপত্তা দেয়া হয়েছে। কিন্তু ইসলামী ভাবধারা জাগ্রত করার সকল প্রচেষ্টা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অথচ ঐ দেশটি নিজেকে তথাকথিত “স্বাধীন বিশ্বের অঙশ” বলে বিবেচনা করে। আরো মারাত্মক হচ্ছে ঐ দেশটির মুসলিম নেতা-কর্মীদেরকে কারাগারে নিক্ষেপ করে নিষ্ঠুর নির্যাতন চালানো হচ্ছে। তাদের বিরুদ্ধেও একমাত্র অভিযোগ, তারা আল্লাহ্ কে প্রভু, সত্যকে লক্ষ্য, ইসলামকে একমাত্র পথ, কথাকে অস্ত্র এবং জ্ঞানকে তাদের একমাত্র খোরাক বলে ঘোষণা করেছিলো।
অতএব, হেকমত ও সুন্দর ভাষণের মাধ্যমে ইসলাম প্রচারে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে তরুণরা যদি শক্তিকে ও সহিংসতাকে সহিংসতা দিয়ে মোকাবিলা করতে চায় তাহলে কি তাদের দোষ দেয়া যায়? এই অবস্থা চলতে দেয়া যায় না। ইন্ শাআল্লাহ ইসলাম যেভাবে হোক সংঘবদ্ধভাবে এগিয়ে যাবে। তাদেরকে সুস্থ ও স্বাধীন পরিবেশে কাজ করতে দেয়া উচিত। অন্যথায় ঘটনাবলী অবাঞ্ছিত বিপরীত খাতে প্রবাহিত হতে পারে। খোলাখুলি কাজ করতে না দিলে দাওয়াতী কাজ বিভ্রান্তিকর গোপন সহিংসতা কিংবা চরমপন্থার রূপ নিতে পারে। ক্ষমতাসীন কর্তৃপক্ষের মারাত্মক ভুল হচ্ছে তারা ইসলামী আন্দোলন দমনে বন্দী শিবির সহিংস মানসিক ও শারীরিক নির্যাতনের আশ্রয় নেয়। বন্দীশিবিরগুলোতে মানুষের সাথে পশুর মতো আচরণ করা হয়। এ প্রনঙ্গে ১৯৫৪ ও ১৯৬৫ সালের মিসরের ঘটনা স্মরণ করা যেতে পারে। সামরিক কারাগারে ইসলামী বিপ্লবের নেতা ও কর্মীদেরকে লোমহর্ষক ও অবিশ্বাস্য পন্থায় শাস্তি দেয়া হয়। এখনো এসব কথা দুঃস্বপ্নের মতো মনে হয়। তাদের দেহে আগুন ও সিগারেটের ছ্যাঁক দেয়া হয়, নারী ও পুরুষ বন্দীকে জবাই করা পশুর মতো ঝুলিয়ে রাখা হয়, কারারক্ষীরা পালাক্রমে রক্ত ও পুঁজ জমে না ওঠা পর্যন্ত বন্দীদেরকে আগুনে ঝলসাতে থাকে। এই পাশাবিক আচরণে অনেকেই শাহাদত বরণ করেন। কিন্তু শাস্তিদাতাদের দিল আল্লাহর ভয়ে এতোটুকু কেঁপে ওঠেনি। নাৎসীবাদ, ফ্যাসিবাদ ও সমাজবাদের উদ।ভাবিত সকর নির্যাতন কৌশল তারা নির্বাচারে আল্লাহ্র পথের মুজিহিদদের ওপর প্রয়োগ করে।
এই বন্দীশালায় চরমপন্থা ও তাকফীরের প্রবণতা জন্ম নেয়। বন্দীদের মনে প্রশ্ন জাগে : আমরা কি অপরাধে হচ্ছি? আমরা আল্লাহর কালামের কথা ছাড়া আর কিছুতো বলিনি? আল্লাহর পথে জিহাদে আমরা কেবল আল্লাহ্ রই সাহায্য চেয়েছি, অন্য কারো কাছে তো পুরস্কার বা প্রসঙসা চাইনি? এই প্রশ্ন আরো প্রশ্নের জন্ম দেয়। এই পশুরা কে যারা আমাদের নির্যাতন করে, আমাদের মানব সত্তাকে অপমানিত করে, আমাদের ধর্মকে অভিশাপ দেয়, আমাদের প্রভুরও অমর্যদা করার মতো ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে! একজন পদস্হ কর্মকর্তা একদিন বলে: ‘তোমাদের প্রভুকে আমার কাছে হাযির করো, তাকে আমি জেলে পুরব।” এই পশুগুলোকে কি মুসলমান বলা চলে? এরা যদি মুসলমান হয় তাহলে কুফরী কী? এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, এরাই হচ্ছে কাফির, এদেরকে ইসলামের আওতা থেকে বিতাড়িত করতেই হবে। এরপর আরো প্রশ্নের উদয় হয়: এদের সম্পর্কে এই যদি হয় আমাদের বিচার, তাহলে এদের মনিব সম্পর্কে আমরা কি সিদ্ধান্ত নেবো? ক্ষমতার আসনে বসে যেসব নেতা ও শাসক ইসলামী বিপ্লবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে তাদেরকেই বা কিভাবে বিচার করা উচিত? তুলনামূলক বিচারে তাদের অপরাধ অধিকতর মারাত্মক এবং তাদের রিদ্দাহ আরো স্পষ্ট- যে সম্পর্কে কুরআনুল করীমে বলা হয়েছে: “আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুসারে যারা বিধান দেয় না তারা সত্যত্যাগী।” (৫:৪৭)
এই সিদ্ধান্তে আসার পর ঐ নির্যাতিত মুসলমানরা তাদের সহবন্দীদের কাছে প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয়: যেসব শাসক আল্লাহ্র বিধান মোতাবেক বিচার করে না এবং যারা শরীয়তের বাস্তয়নে সংগ্রামরত তাদের সাথে একমত হলো তাদেরকে শত্রু গণ্য করলো। এমনকি কাফিরও মনে করলো, কেনা কাফিরের কুফরী সম্পর্কে যে সন্দেহ পোষণ করে সে নিজেই কাফির। কিন্তু একানে শেষ নয়। যেসব লোক ঐরূপ শাসকের আনুগত্য করে তাদের সম্পর্কেও প্রশ্ন উঠলো। জবাব তৈরি ছিলো: তাদের শাসকের আনুগত্য করে সে নিজেও কাফির।
এভাবে ব্যক্তি গ্রুপ বিশেষকে কুফরী ফতোয়া দেয়ার্ প্রবণতা মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো। লক্ষণীয় ব্যাপার হচ্ছে, সহিংসতা শুধু সহিংসতার জন্ম দেয় না, সুস্থ চিন্তাকেও দূষিত করে এবং ঐ দলন-দমন অর্নিবার্য বিদ্রোহের জন্ম দেয়।
পরিভাষা সঙ্কেত
১. সুনান: রীতি, ধারা।
২. তালিব আল-হাদীস:
যে বৈশিষ্ট্য ও পরিস্থিতিতে হাদীস অশুদ্ধ হতে পারে সেই সংক্রান্ত শাস্ত্র।
তৃতীয় অধ্যায়
চরমপন্থার প্রতিকার
এখন আমরা চরমপন্থার প্রতিকার এবং তার উপায় ও পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করবো। প্রথমেই এ বিষয়টি বুঝে নেয়া দরকার যে, প্রতিকার চরমপন্থার কারণ থেকে অবিচ্ছিন্ন। এর কারণগোলো যেমন বিভিন্ন ও জটিল তেমনি এর প্রতিকারগুলোও। বলা বাহুল্য, কোনো যাদুস্পর্শে চরমপন্থার অবসান ঘটানো যাবে না কিংবা তাদেরকে মধ্যপন্থা ফিরিয়ে আনা যাবে না। আমাদের কাছে চরমপন্থা ও গোঁড়ামি-এর মনস্তাত্ত্বিক, সামজিক ও রাজনৈতিক দিকসহ একটি অদ্ভুত ধর্মীয় সমস্যা। সুতরাং ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে এর সবগুলো দিক বিবেচনা করতে হবে।
আমি তাদের সাথে একমত নই যারা কেবল সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থাকে এই অদ্ভুত সমস্যার কারণ বলে চিহ্নিত করে যুব সমাজের আচরণ ও পদক্ষেপগুলো উপেক্ষা করতে চান। আবার সমাজ, সরকার, সরকারী বিভাগ, বিশেষত শিক্ষা ও প্রচার মাধ্যমকে সকল দায়-দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়ে কেবর যুব সমাজকে দোষ দেয়া অন্যায়। দায়িত্বটা আসলে পারস্পরিক এবং প্রতিটি পক্ষের একেকটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, “তোমরা সকলে তোমাদের সন্তান-সন্ততি ও অধীনস্থ ব্যক্তিদের অভিভাবক এবং দায়িত্বশীল।” (বুখারী)
আমরা এখন চরমপন্থা কাটিয়ে ওঠার ব্যাপারে সমাজের পরিপূরক ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করবো। আমি আগেই বলেছি, বর্তমান যুগের অন্তর্গত পরস্পর বিরোধিতা ও অরাজক অবস্থা এবং ইসলাম থেকে মুসলমানদের বিচ্যুতি চরমপন্থা প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। অতএব, এই সামজকেই এর প্রতিকারে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে হবে। প্রাথমিক পদক্ষেপ হচ্ছে, ইসলামের প্রতি তাদের আন্তরিক, সুদৃঢ় ও সুষ্পষ্ট অঙ্গীকার নবায়ন করা। এটা কেবল মৌখিক ঘোষণা, কিছু মনোহর শ্লোগান অথবা সংবিধানে ‘ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম’ ঘোষণা করে নয়, বরং ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার ঘনিষ্ঠ অনুসরণের মাধ্যমেই সম্ভব।
আমরা জানি, ইসলাম এমন একটি সার্বিক জীবন বিধান যা মানুষের মধ্যে ঐশী বৈশিষ্ট্যকে বিকশিত করতে চায়। এ জন্যে ইসলাম জীবনকে সঠিক পথে পরিচালনা ও বিচ্যুতি থেকে রক্ষার লক্ষ্যে আদর্শিক কাঠামো, পথ-নির্দেশ ও সীমারেখা নির্ধারণ করে দিয়েছি। এর আওতায় থাকলে মানুষের এবাদত-বন্দেগী, মনমানস, আইন-বিধান এক সৌন্দর্যময় রূপ লাভ করে, এক সুবিচারপূর্ণ সমাজ গড়ে ওঠে। তাই প্রকৃত ইসলামী আদর্শের বাস্তবায়ন করতে হবে। ইসরাঈলদের মতো খন্ডিতভাবে নয়। আল্লাহ তায়লা কুরআনুল করীমে বলেন:
“তাহলে তোমরা কি কিতাবের কিছু অংশ বিশ্বাস করো এবং কিছু অংশ প্রত্যাখ্যান করো? সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা এরূপ করে তাদের একমাত্র প্রতিফল পার্থিব জীবনে জিল্লতি আর কিয়ামতের দিনে তারা কঠিনতম শাস্তির দিকে নিক্ষিপ্ত হবে।” (২:৮৫)
সুতরাং ইসলামী চরিত্রের সমাজ কায়েম করতে হলে জীবনের সর্বক্ষেত্রে তথা সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষেত্রে আল্লাহ্ র বিধান ও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সুন্নাহ প্রয়োগ করতে হবে। এটাই ঈমানের প্রকৃত দাবী। কুরআনের ঘোষণা:
“কিন্তু না, তোমার প্রভুর শপথ! তারা মুমিন হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের নিজেদের বিবাদ-বিসম্বাদের বিচারের ভার তোমার ওপর অর্পণ না করে; অতঃপর তোমার সিদ্ধান্ত সম্পর্কে তাদের মনে কোন দ্বিধা না থাকে এবং সর্বান্তঃকরণে তা মেনে নেয়।”(২৪:৫১)
আমরা ইসলামকে ঐশী বিধান হিসেবে মানি। কিন্তু বাস্তব জীবনে শরীয়াহকে প্রয়োগ করি না। তার জায়গায় আমরা পূর্ব ও পশ্চিম থেকে ধার করা ব্যবস্থা চালু করেছি, তবুও আমরা মুসলমান বলে দাবী করি! সমাজ থেকে এই সুষ্পষ্ট পরস্পর বিরোধিতা অবশ্যই দূর করতে হবে।
সুতরাং আমেদের শাসকদের অনুধাবন করতে হবে যে, তারা মুসলিম ভূখন্ড শাসন করছেন এবং মুসলমানদের তাদের ধর্মীয় বিধান অনুসারে শাসিত হওয়ার অধিকার আছে। সামাজিক, রাজনৈতিক, বুদ্ধিবুত্তিক, সাংস্কৃতিক, আন্তর্জাতিক তথা সকল ক্ষেত্রে ইসলামী মূল্যবোধের প্রতিফলন ঘটাতে হবে।
সকল ও আন্তর্জাতিক নীতি এই বিশ্বাসের ভিত্তিতে প্রণয়ন করতে হবে। মুসলিম শাসকরা যদি এই ন্যায়সঙ্গত প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ হন তবে তা হবে চরম ইসলাম বিরোধিতার শামিল। বস্তুত এ বিষয়টির প্রতি মুসলিম শাসকদের উপেক্ষা ও ঔদাসীন্য অসহনীয় হয়ে উঠেছে। কেউ কেউ প্রকাশ্যে ইসলামী আন্দোলনকারীদের সকল সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত করেন। এই শাসকরা মসজিদকেও তাদের মতলব হাসিলের কাজে লাগান। কেউ এর বিরোধিতা করলে তাকে কঠোর শাস্তি দেয়া হয়। আবার কিছু কিছু শাসক মুসলমান বলে দাবী করেন এবং যা তাদের ধারণা নেহায়েত মনগড়া এবং শয়তানী খেয়ালখুশীর নামান্তর। যা তাদের মতলব হাসিলের অনুকূল তা গৃহণ করেন এবং তাদের পছন্দসই নয় তা নির্দ্বিধায় নাকচ করে দেন। তারা যা বিশ্বাস করেন তাকেই “সত্য” বলে ঘোষণা করেন এবং এর বিপরীত সবকিছু বাতিল। তারা কুরআন ও হাদীসের সঠিক ব্যাখ্যা অস্বীকার করে নিজেরাই এ সবের ব্যাখ্যাতা সাজেন। তারা কোনো বিজ্ঞ আলিম-ওলামার সাথে পরামর্শ করার ধার ধারেন না। তারা প্রত্যেক নিজেকে একেকজন ফকীহ, মুফাসসির, মুতাকাল্লিম ও দার্শনিক ভেবে বসেন।
এ ধরনের মুসলমান শাসক মনে করেন তাদের বিকল্প দ্বীতিয় ব্যক্তি নেই। তিনি হযরত মুহাম্মদ (সা) থেকেও কিছু শেখার প্রয়োজন অনিভব করেন না। কুরআন ব্যাখ্যার জন্যে তিনি নিজেকেই যথেষ্ট মনে করেন। অথচ আল্লাহ্ বলেন: “রাসূলের আনুগত্য করে, সে আল্লাহ্র আনুগত্য করে।” (৪:৮০)
অবশ্য এসব শাসক ব্যক্তিগত জীবনে ইসলামী শরীয়াহ প্রয়েগের অনুমতি দেন। রেডিও-টেলিভিশনে ইসলাম সম্পর্কে আলোচনার কিঞ্চিত সুযোগ দিয়ে থাকেন আর সংবাদপত্রে শুক্রবারের জন্যে একটি কালাম বরাদ্দ করেন। এখানে অলোচ্য বিষয় হচ্ছে ধর্ম কেবল ব্যক্তি সত্তা ও স্রষ্টার সম্পর্কের মধ্যে সীমিত। সমাজ ও রাষ্ট্রের সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই। এটাই হচ্ছে অধুনা মুসলিম শাসকদের বিশ্বাস অথাৎ আইন ছাড়া ঈমান, রাষ্ট্র ছাড়া দ্বীন, দাওয়াত ছাড়া ইবাদত এবং সত্যের আদেশ ও মিথ্যার নিষেধ ছাড়া জিহাদের ডাক। এখন কোনো নাগরিক যদি এদের বিরোধিতা কের ইসলামী জীবন বিধান চালুর ডাক দেয় তবে তার বিরুদ্ধে ধর্ম ও রাজনীতি সংমিশ্রণের অভিযোগ আনা হয়। মোটকথা, শাসকদের কর্যকলাপ আল্লাহ্, আল্লাহ্ র রাসূর ও তাঁর সাহাবীদের পথের বিপরীত। মুসলিম বিশ্ব এক চরম সন্ধিক্ষণে। অতএব, প্রকৃত ইসলামের প্রতি অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়ে তা প্রতিষ্ঠা করা ছাড়া সমাজে স্থিতিশীলতা আসতে পারে না. পারে না জনগণের প্রত্যাশা পূরণ করতে। উমর ইবনে খাত্তাব (রা) বলেন, “আমরা নিকৃষ্টতম জাতি ছিলাম। কিন্তু ইসলাম দিয়ে আল্লাহ আমাদেরকে স্মানিত করেছেন। যদি আমরা ইসলামকে বাদ দিয়ে অন্য পন্থায় মর্যাদা হাসিল করতে চাই তবে আল্লাহ্ আমাদের গোড়া কেটে দেবেন।” সুতরাং শারীয়াহ প্রয়োগ না করা পর্যন্ত আমাদের সমাজে চরমপন্থার বিস্তার ঘটবেই।
দ্বিতীয় পদক্ষেপ হচ্ছে, তরুণদের প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টাতে হবে। আইভরি টাওয়ার থেকে তাদের উদ্দেশ্যে মুরব্বীসুলভ ভাষণ দিলে চলবে না। তাদের মনমানসিকতা ও বাস্তবতা উপলব্ধি করে কথা বলতে হয়। নইলে তারা কথা শুনতেই অস্বীকার করবে। তাদের শুধু দোষ দিয়ে থাকেন। শুধু তাই নয়, তাদের গুণগুলো উপেক্ষা করে দোষগুলোই প্রচার করা হয়।
তৃতীয়ত, আমাদের সমাজে আরেকটি প্রবণতা রয়েছে। একটা গোষ্ঠীর কেউ একজন দোষ করলে তা সাধারণভাবে সকলের ওপর চাপানো হয়। তরুণদের বেলায় এটি আরো বেশী প্রযোজ্য। একজন তরুণ করলো কী করলো না, অমনি তা সকল তরুণদের ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়। তাছাড়া ঘটনা ভাল করে না জেনে হুট করে রায় দেয়ারও প্রবণতা আমাদের রয়েছে। ভাল করে না জেনে না শুনে সংখ্যালঘৃর দোষ সংখ্যাগুরুর ওপর চাপিয়ে দেয়া ন্যায় বিচার নয়। এজন্যে মুসলিম ফকীহরা রায় দিয়েছেন, সংখ্যাগুরুর বিরুদ্ধে যে রায় দেয়া হয় তা সার্বিকভাবে প্রযোজ্য, কিন্তু এর বিপরীতটা নয় অর্থাৎ মুষ্টিময়ের বিরুদ্ধে প্রদত্ত রায় সংখ্যাগুরুর বিরুদ্ধে প্রযোজ্য হতে পারে না। একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে একজনের সামগ্রিক কর্মকান্ডের বিচার হতে পারে না। তার সামগ্রিক আচরণের মূল্যায়ন করেই তার সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া যায়। কারণ কুরআন বলছে: “যার (সৎকর্মের) পাল্লা ভারী, সেই মুক্তি পাবে।” (২৩:১০২)
চতুর্থ, নিছক ব্যক্তিগত বিশ্বাস দিয়ে তরুণদের বিচার করা ঠিক নয়। তাদেরকে অনেক মানসিক রোগজনিত খামখেয়ালি বলে ভাবেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এটা সত্য হতে পারে; কিন্তু সামগ্রিকভাবে সন্দেহাতীত। আসলেই তাদের ঈমান ও আচরণে কোনো দ্বৈততা নেই। আমি অনেক মুসলিম দেশের অনেক তরুণের কথা জানি, তারা ঈমানী জযবায় সুদৃঢ় এবং আমলে-আচরণে সত্যনিষ্ঠ। সত্যের প্রতি তাদের নিষ্ঠা ও মিথ্যার প্রতি তাদের র্ঘণাকে আমি প্রশংসাকরি। তারা সমাজে ইসলামী মূল্যবোধ ও শারীয়াহ প্রতিষ্ঠার জন্যে কঠোর জিহাদে নিমগ্ন। এই তরুণদের সাথে মেলামেশা করে আমার স্থির বিশ্বাস জম্মেছে যে, আমাদের পোচলিত ইসলামী ধ্যান-ধারণার সাথে তাদের চিন্তাধারার মৌলিক পার্থক্য আছে। তারা এক নতুন উদ্দীপ্ত ইসলামের প্রতি অঙ্গীকারাবদ্ধ যে ইসলাম আমাদের মতো জরাজীর্ণ নয়; তাদের ঈমান সতেজ, আমাদেরটা ঠন্ডা; তাদের সাধুতা সুদৃঢ়, আমাদেরটা করুণ। তাদের হৃদয়ে আল্লাহ্ র ভয় সদাজাগ্রত- তাদের হৃদয় কুরআনের তিলাওয়াতে সদা স্পন্দিত। তাদের মধ্যে কেউ কেউ সারা রাত ইবাদতে মগ্ন থাকে, দিনে রোযা রাখে, প্রত্যুষে আল্লহ্ র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে। এসব দেখে আমার পূর্ণ বিশ্বাস জন্মেছে যে, ইনশাআল্লাহ্ ইসলাম আবার স্বীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হবে। এ জন্যেই আমি মিসরে বিভিন্ন উপলক্ষে ঘোষনা করেছি, এই তরুণ গোষ্টীই মিসরের প্রকৃত আশার আলো। যে কোনো বৈষয়িক সম্পদের চেয়ে এরা অধিক মূল্যবান।
তাই আমি বিশ্বাস করি, চরমপন্থার প্রতিকার অন্বেষণে আমাদের কথাবার্তায় আচরণে বারসাম্য, সুবিবেচনা ও উদারতা থাকতে হবে। এলোপাথাড়ি অতশয়োক্তি এই অদ্ভুত সমাধানের সহায়ক হবে না, করং এই প্রকণদা ত্রাস সৃষ্টি করে। সবচেয়ে বড় কথা, সত্য ও প্রকৃত ঘটনাকে বিকৃত, বিচারের মানদন্ডকে দোদুল্যমান এবং সুস্থ চিন্তাকে দূষিত করে। ফলত কনো, তা অন্যায় কিংবা অন্তত অসম্পূর্ণ হতে বাধ্য।
তাথাকথিত “ধর্মীয় চরমপন্থা” এবং সরকার ও তরুণদের মধ্যে সংঘাতের ফলে উদ্ভুত সংকট মুকাবিলার প্রক্ষিতে যা কিছু বলা বা লেখা হচ্ছে তা বাড়াবাড়ি ও অতিশয়োক্তি মুক্ত নয়। তরুণদের বিরুদ্ধে অনেক মানুষ অসদুদ্দেশ্য-প্রণোদিত মনোভাব পোষন করে। ঐসব বক্তব্যে এর প্রভাব লক্ষণীয়। এই প্রসঙ্গ নিয়ে একজন সমাজবিজ্ঞানী ড. সাদ আল দ্বীন ইবরাহীম ‘আল-আহরাম’ পত্রিকায় লিখেছেন: যারা এই প্রচারণায় অংশ নিয়েছেন তারা আসল সত্যের ধারে কাছেও নেই। তাদের যুক্তির কোনো সুনিদৃষ্ট ভিত্তিও নেই। তাদের বক্তব্যে অজ্ঞতা ও চরম অবিবেচনাপ্রসূত দৃষ্টিভঙ্গি প্রকট। প্রকৃতপক্ষে এই সমস্যার প্রশ্নে এদের নিশ্চুপ থাকাই শ্রয় ছিলো, নতুবা বাস্তব দৃষ্টিকোন থেকে সমস্যার বিশ্লেষণ করা উচিত ছিলো। কিন্তু এই গুণ বৈশিষ্ট্য তো এদের মধ্যে নেই। এ ব্যাপারে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে, ধর্মীয় ব্যাপারে এসব লোকের মুক্তকচ্ছ, শিথিল ও ঔদাসীন্যের চরমপন্থী মনোভাবই ধর্মীয চরমপন্থা সৃষ্টিতে সহায়ক হয়েছে। মোটকথা, এক শ্রেনির লোকের চরম বিরাগ আরেক শ্রণিকে চরম অনুরাগী করেছে। যদা কোনো বিজ্ঞ প্রচেষ্টা উভয়পক্ষের মতভেদ দূর করে তাদেরকে একত্র করতে ব্যর্ত হয় তাহলে এটাই প্রমানিত হয় যে, সমাজে ভারসাম্য সৃষ্টর জন্যে এক চরমপন্থা নির্মূলে আরেক চরমপন্থারই প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে কুরআন শরীফে একটি ধারণা পাওয়া যায়:
“যদি আল্লাহ্ তায়ালা একটি জনগোষ্টী দিয়ে আরেকটি জনগোষ্টিকে প্রতিহত না করতেন তাহলে পৃথিবী বিপর্যস্ত হয়ে যেতো; কিন্তু আল্লাহ্ জগতসমূহের প্রতি অনুগ্রহশীল।” (২: ২৫১)
সুতরাং তরুণ মুসলমানদের প্রতি অভিযোগ অযৌক্তিক, যখন প্রতিপক্ষ চরমপন্থীরা ধর্ম ও নৈতিকতা বিগর্হিত জীবনের গড্ডালিকা প্রবাহে ভেসে যাচ্ছে। যেসব তরুণ ইসলামী শিক্ষা অনুযায়ী তাদের জীবন গড়ে তুলতে প্রয়াসী তাদেরকে হেয় করার প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ অযৌক্তক ও অন্যায়। যেসব তরুণ পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ছে, রোযা রাখছে, দাড়ি রাখছে, গিরার উপর কাপড় পরছে, হালাল হারাম বিবেচনা করছে, ধুমপান থেকে বিরত থাকছে তাদেরকে দোষ দেয়ার বা নিন্দা করার কী যুক্তি থাকতে পারে। অথচ আমরা নীরবে চোখের সামনে দেখি একদল লোক জীবনকে উপভোগ করে চলেছে নির্বিচারে। নৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক দিক দিয়ে পাশ্চাত্যের এই মানসপুত্ররা সম্পূর্ণ উচ্ছন্নে গেছে। অতএব ধর্মীয় “চরমপন্থার” বিরুদ্ধে “গেলো গেলো রব” তোলা আর “ধর্মহীন চরমপন্থা” র পক্ষে চোখ কান বুজে থাকা যুক্তির কোন্ মানদন্ডে সঙ্গত? মেয়েরা পর্দা করে চলাফেরা করলে উপহাসের পাত্রী হতে হয়; কিন্তু যখন আরেক দল মেয়ে রাস্তাঘাচে, সৈকতে, থিয়েটারে, সিনেমায় প্রায় উলঙ্গভাবে নিজেকে প্রদর্শন করে তখন তাকে “সংবিধানসম্মত ব্যক্তি স্বাধীনতা” ভোগ বলে পার পাওয়া কী উচিত? তাহলে কী ধরে নিতে হবে, সংবিধানে নগ্নতা ও বেহায়াপনার জন্যে ব্যক্তি স্বাধীনতার অনুমতি দেয়া হয়েছে, আর সতীত্ব ও শালীনতা নিষিদ্ধ করা হয়েছে? সমাজ যদি অনৈতিক ও ধর্মহীন তৎপরতা প্রতিরোধে এগিয়ে আসতো তাহলে আমাদের দেশে ধর্মীয় চরমপন্থা’র উদ্ভব হতো না, যদিও কোনো না কোনো কারণে চরমপন্থা বিরাজ করতে তাহলে এর প্রবাব হতো নগণ্য। আমাদের এটা স্বীকার করতে হবে ‘চরমপন্থা’ একটি বিশ্বজনীন ঘটনা; কিন্তু মজার ব্যাপার বিভিন্ন দেশে আন্যান্য চরমপন্থী গ্রুপ বা সংগঠন থাকলেও তাদের বিরুদ্ধে এ রকম চরম পদক্ষেপ নেয়া হয় না। কিন্তু যত দোষ কেবল মুসলমানদের বেলায়। তারা চরমপন্থী হলে তাদের বিরুদ্ধে নানা অজুহাতে চরম নির্যাতনের পথ বেছে নেয়া হয়। ইসরাঈলের চরমপন্থী ইহুদীরা মনে করে ঐ ভূমিতে তাদের ঈশী অধিকার রয়েছে এবং এই লক্ষ্যে তারা সকল রকম হিংস্র তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। অথচ খোদ ইসরাঈলের সৃষ্টিটাই অবৈধ এবং সন্ত্রাসী কাজ। লেবাননে খ্রীস্টান ফালাজির চরম সহিংস পন্থায় মুসলমানদের ওপর নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে। তারা মুসলমানদের যবাই করছে, তাদের লাশ ক্ষতবিক্ষত করছে, গুপ্ত অঙ্গ কেটে তাদেরই মুখে পুরে দিচ্ছে, মুসলমানদের ধর্মীয় বইপুস্তক পুড়িয়ে ফেলছে। খ্রীস্টানদের ধর্মীয় গ্রন্থে বলা হয়েছে, “তোমার শত্রুকে ভালবাসো, তোমাকে যারা ঘৃণাকরে তাদের ভাল করো, কেউ তোমার ডান গালে চড় মারলে বাম গালও পেতে দাও।” (লুক ৬ : ২৭-২৯)।
এছাড়া আমরা অন্যান্য দেশ, যেমন সাইপ্রাস, ফিলিপাইন ও হিন্দুস্থানে মুসলমানদের বিরুদ্ধে সন্তাসী তৎপরতা দেখতে পাই। মুসলমানদের বিরুদ্ধে এক সর্বাত্মক খ্রীস্টানী সন্ত্রাস শুরু হয়েছে যাকে বলা যায় নতুন ক্রুসেড। প্রতি বছর হিন্দু চরমপন্থীরা মুসলমানদের ওপর হত্যাযজ্ঞ চালাচ্ছে। পরিহাসের বিষয়, হিন্দুরা প্রাণী হত্যাকে নির্দয় নিষ্ঠুর কাজ বলে মনে করে। এ জন্যে তাদের ধর্মে গরু যবাই নিষিদ্ধ। কিন্তু এরাই আবার ঠাণ্ডা মাথায় মানুষ হত্যা করে চলেছে বেধড়ক! একই কারণে তারা আবাদী জমিতে নাকি কীটনাশক ব্যবহার করে না। লাখ লাখ একর জমির ফসল তাই ইঁদুরের পেটে চলে যায়। তাদের দৃষ্টিতে এসব প্রাণীরও আত্মা আছে, তাই তাদের আঘাত করা যাবে না। তাদের দৃষ্টিতে বোধ হয় একমাত্র মুসলমান নামক প্রাণীরই আত্মা নেই!
একথাও আমাদের স্বীকার করতে হবে, বস্তুবাদ মানুষের চিন্তাও আচরণকে বিকৃত করে ছেলেছে। বিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের চরম উন্নতি হয়েছে, মানুষ চাঁদেও গেছে, গ্রহান্তরে আধিপত্য বিস্তার করছে। কিন্তু এসব বৈষয়িক উন্নতির পাশাপাশি আত্মার উন্নতি হয়নি। বিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের চরম উন্নতি হয়েছে, মানুষ চাঁদেও গেছে, গ্রহান্তরে আধিপত্য বিস্তার করছে। কিন্তু এসব বৈষয়িক উন্নতির পাশাপাশি আত্মার উন্নতি হয়নি। ফলে মানুষ আজ মনের সুখ পাচ্ছে না। এক সমায় তারা মনে করেছিলো বস্তুগত আরাম-আয়েশ লাভ করতে পারলে মনের শান্তিও পাওয়া যাবে। কিন্তু তাদের সে আশার গুড়ে বালি! তাদের মধ্যে চরম নৈরাজ্য দেখা দিয়েছে। হিপ্পি জাতীয় নানা গ্রুপ নিত্য নতুন গজাচ্ছে তাদের কাছে আধুনিক সভ্যতা অর্থহীন হয়ে পড়েছে, তারা এখন প্রকৃতিতে ফিরে যেতে চায়। তাদের মনে প্রশ্ন জেগেছে : আমি কে? আমার লক্ষ্য কি? আমি কোথা থেকে এসেছি? এখন থেকে আমাকে কোথায় যেতে হবে? কিন্তু পাশ্চাত্যের কাছে এসব প্রশ্নের জবাব নেই। এমনি নৈরাজ্যের প্রতিধ্বনি আমাদের দেশেও শোনা যায় এই প্রশ্নের জবাব নেই। এই প্রশ্নের জবাব পেতে গিয়ে কেউ চরম বিধর্মি হয়ে গেছে, আবার কেউবা সত্য পথের সন্ধান পেয়ে ইসলামের সুশীতল চায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। সুখের বিষয়, বহু মুসলিম তরুণ সকল প্রশ্নের সছিক উত্তর ইসলামের মধৈই খুঁজে পেয়ে নিজেদের জীবনকে ইকামতে দ্বীনের জন্যে কুরবানী করতে প্রস্তুত।
আজকের বিশ্বে চারদিকে হিংসা আর বিদ্রোহের বহ্নি। এর মাঝে শান্তি, নমনীয়তা ও ভারসাম্য প্রত্যাশা করা অসঙ্গত। উৎসাহী তরুণদের কাছ থেকে মিরব্বীদের মতো প্রজ্ঞা ও পরিণত চিন্তা আশা করা যুক্তিসঙ্গত নয়। মানুষ প্রাথমিকভাবে পরিবেশেই সৃষ্টি। গুপ্ত পুলিশকে কঠোর ব্যবস্থা, নির্যাতন ও গুপ্ত হত্যা বন্ধ করতে হবে। স্বাধীনতা, সমালোচনা ও পারস্পরিক পরামর্শের অধিকার দিয়ে সুস্থ পরিবেশ সৃষ্টিতে উদ্যোগী হতে হবে। হযরত উমর (রা)-এর একটি কথায় আমরা এর নযীর পাই: “আল্লাহ্ তাদের রহম করুন যারা আমার ত্রুটিগুলো দেখিয়ে দেয়।” তাই তিনি তাকে পরামর্শ দানে ও তার সমালোচনা করতে সকলকে উৎসাহ দিতেন। একদিন এক ব্যাক্তি হযরত উমর (রা) কে বলেন, “হে খলীফা, আল্লাহ্ কে ভয় করুন!” উমর (রা)-এর সঙ্গীরা ত্রুদ্ধ হলেন। কিন্তু হযরত ওমর (রঅ) লোকটিকে নির্দ্বিধায় বলতে দিলেন এবং তাঁর সঙ্গীদেরকে বললেন, “তোমরা যদি (এই লোকটির মতো) কথা না বলো তাহলে তাতে কল্যাণ নেই এবং আমাদের (শাসকদের) মধ্যেও কোনো কল্যাণ নেই যদি আমরা তোমাদের (পরামর্শ ও সমালৌচনা) না শুনি।” আরেকবার উমর (রা) শ্রোতাদের উদ্দেশ্য বললেন, “তোমাদের মধ্যে বিচ্যুতি দেখে তাহলে আমকে সঠিক পথে আনার দায়িত্ব তারই।” এ কথা শুনে একজন লোক উঠে দাঁড়িয়ে বলল, “আল্লাহর শপথ, আপনার মধ্যে আমরা যদি আমার মধ্যে বিচ্যুতি দেখি তাহলে এই তোলয়ার দিয়ে আপনাকে ঠিক করব। (অথাৎ বল প্রয়োগ)।” উমর (রা) রাগ না খুশী হয়ে বললেন: “আলহ্মদুলিল্লাহ, মুসলমানরা তলোয়ার দিয়ে উমরকে ঠিক পথে আনার জন্যে তৈরি আছে।” বস্তুত স্বাধীন পরিবেশ থাকলে নানা মতের উদ্ভব ঘটে এবং সেগুলো নিয়ে সাধারণ মানুষসহ বিচক্ষণ ব্যাক্তিরা আলাপ-আলোচনা করে ভালটা গ্রহণ ও মন্দটা বর্জন করতে পারেন। ফলে অপ্রীতিকর মতভেদের আশাঙ্কাও তিরোহিত হয়।
অন্যথায় চরমপন্থী ভাবধারা গোপনে সুপ্ত বীজের মতো বাড়তে বাড়তে মহীরুহে পরিণত হয়। অবশেষে একদিন সহিংস তৎপরতার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়ে সকলকে হতবাক করে দেয়। মন ও মেধা চরমপন্থী চিন্তাধারার উৎস। এর মুকাবিলায়ও মন ও মেধা প্রয়োজন। শক্তি প্রয়োগ করে এর মুকবিলা করতে গিয়ে হিতে বিপরীত হয়। সতর্কতা, ধৈর্য ও বুদ্ধিবৃত্তিক কৌশল অবলম্বন করেই চরমপন্থী মনোভাব পাল্ঠাতে হবে। কিন্তু সাময়িক অভ্যুথ্থানের নেতৃবৃন্দ এখানেই ভুল করে বসেন। তারা তাদের গুপ্ত পুলিশ লেলিয়ে দিয়ে তাদের প্রতিপক্ষের ওপর নিষ্ঠুর কায়দায় নির্যাতন চালান। এতে তারা সাময়িক সাফল্য অর্জন করেন বটে, কিন্তু চরমপন্থা দমনে শেষতক চরমভাবে ব্যর্থ হন। কেননা একটা চরমপন্থা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে।
অতএব, এই পর্যায়ে আমাদের প্রথম কর্তব্য হচ্ছে বুদ্ধিদীপ্ত ফিকাহর ভিত্তিতে যুক্তিগ্রাহ ইসলামী জাগরণ সৃষ্টি করতে হবে। এই ফিকহ শুধু ছোটখাট বিষয় নয়, বরং অপরিহার্য দিকগুলোর প্রতি মনোযোগ দেবে এবং খন্ড ও অখন্ড, শাখা ও মূল, মূর্ত ও বিমূর্ত বিষয়গুলোর যথার্থ রূপভেদ ব্যাখ্যা করবে। এ ধরনের ফিকহর বিকাশ সহজ কাজ নয়। মানুষের ধ্যান-ধরণায় পরিবতর্ন তথা কোন্টি সঠিক, কোন্টি ভুলতা বিচারের মানসিকতা গড়ে তোলার জন্যে আন্তরিক প্রয়াস, পচন্ড ধৈর্য এবং আল্লাহ্ তায়ালার সাহায্য দরকার।
ক্ষমতাসীনরা মনে করে, রেডিও-টিভিকে কাজে লাগিয়ে তাদের ইচ্ছা মাফিক গণমানস পরিবর্তন করা সম্ভব। কিন্তু মানুষ এ ধরনের সরকারী প্রচার কৌশলে আস্থা আনতে পারে না। বিভিন্ন দেশের সরকার কিছু ওলামা ও বাগ্মীকে এই কাজে লাগানোর চেষ্টা করেছেন, বিশেষ করে বন্দীদের চিন্তাধারা পরিবর্তনের চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু সকল প্রচেষ্টা নিদুরুণভাবে ব্যর্থ হয়েছে। একমাত্র সরকারী প্রভাবমুক্ত হাক্কানী আলিমরাই এই অবস্থার পরিবর্তন করতে পারেন। এসব মুক্ত হাক্কানী আলিম তাদের জ্ঞানের মৌলিকতা ও গভীরতার জন্যে যুব সামাজ তথা সাধারণ মানুষের আস্থা ও শ্যদ্ধাভাজন। কিন্তু এ জন্যে সন্ত্রাসমুক্ত স্বাভাবিক পরিবেশ দরকার। মুক্ত ও গঠনমূলক আলোচনা, পারস্পরিক যোগাযোগ ও ভাবের আদান-প্রদানের মাধ্যমেই সঠিক চিন্তার বিকাশ ঘটা সম্ভব। আদেশ-নিষেধ জারি করে রাতারাতি মনের রূপান্তর সম্বব নয়।
এ প্রসঙ্গে আমি যে বিষয়টির উপর গুরুত্ব দিতে চাই তা হচ্ছে একটি বুদ্ধিবৃত্তিক সন্ত্রাসকে আরেকটি বুদ্ধিবৃত্তিক সন্ত্রাস দিয়ে মুকাবিলার বিপদ অথাৎ একগুয়েমির সাথে একগুয়েমি, গোঁড়ামির সাথে গোঁড়ামি এবং অপকর্মের সাথে অপকর্মের মুকাবিলা। উদাহরণস্বরূপ পরস্পরের বিরূদ্ধে কুফরীর অভিযোগের কথা উল্লেখ করা যায়। এর সপক্ষে একটি হাদীসের কথা বলা হয়, “যে ব্যক্তি একজন মুসলমানকে কাফির বলে সে নিজেই কুযফরী করে।” কোনো বিষয়ে ব্যাখ্যার ভুল, সন্দেহ বা ভূল সিদ্ধান্তের জন্যে একজন মুসলমানকে উক্ত হাদীসের আলোকে কাফির বলে অভিযুক্ত করা যায় না। হাদীস ও সাহাবীদের জীবন থেকে আমরা এর প্রমাণ পেতে পারি। হযরত আলী (রা) খারিজীদের কেবল নিন্দাই করেছেন কিন্তু কাফির বলেননি। খারিজীরা তাকে কাফির বলে ফতোয়া দিয়েছিল। তিনি তাদের নিয়তকে ভাল মনে করে তাদেরকে ইসলামের আওতার মধ্যেই রেখেছিলেন। তাই তাঁকে যখন জিজ্ঞেস করা হয়েছিল খারিজীরা কাফির কিনা তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছিলেন, তারা কুফরঅ থেকে বেঁচে গেছে, তারা অথীতে আমাদের ভাই ছিল, আজ তারা ভূল করেছে। এর অর্থ আলখাওয়ারিজকে কাফির বা মুরতানিন না বলে বাগী বলে গণ্য করা যায়। এই ক্ষত্রে বুগাতের তাৎপর্য দাঁড়ায় ভুল ব্যাখ্যা ভিত্তিতে যে ব্যক্তি ন্যায়পরায়ণ মুসলিম ইমামের আনুগত্য করে না। এ ধরনের বাগীদের বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিকভাবে যুদ্ধ করা সমীচীন নয়, বরং সকল পন্থায় তাদেরকে সংশোধনের উদ্যোগ নিতে হবে। যুদ্ধ করতে হবে। যুদ্ধ ক্ষেত্রে যদি তারা বিপর্যস্ত হয় তাহলে তাদের সাথে কর্কশ আচরণ-নির্যাতন করাও উচিত হবে না। কেননা তাদেরকে নির্মূল করা নয়, বরং ইসলামের আওতায় ফিরিয়ে আনাই সকল প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য। অতএব তাদেরকে মুসলমান হিসেবেই গণ্য করতে হবে।
হযরত আলী (রা)-এর আমলে মত প্রকাশের স্বাধীনতাও ছিল নজিরবিহীন, সে অবস্থায় পৌঁছতে অনান্য দেশকে আরো বহু শত্বাদী অপেক্ষা করতে হয়েছেল। আলখাওয়ারিজ হযরত আলী (রা)-এর আপোস মীমাংসা নাবচ করেছিল এই দাবীতে যে, ‘সিদ্ধান্ত কেবল আল্লাহ্রই’। আলী (রা) তাঁর স্বভাবসিদ্ধ কন্ঠে জবাব দিয়েছিলেন, “বাতিলের স্বার্থে এটা সত্যের বিকৃতি।”তাদের চরম বিরোধিতা সত্ত্বেও আলী (রা) বলিষ্ঠ ভাষায় জানিয়ে দিয়েছিলেন: “আমরা তোমাদেরকে মসজিদে নামায আদায়ে বাধা দেব না, গনমতের মাল থেকে বঞ্চিত করব না, তোমরা যুদ্ধ শুরু না করলে আমরা করব না।”আলী (রা) এমনিভাবে খারিজীদের অথাৎ বিরোধী দলকে সকল অধিকার দিয়েছিলেন অথচ তিনি জানতেন তারা পূর্ণরূপে প্রশিক্ষিত সশস্ত্র সৈন্য, যে কোনো মুহূর্তে অস্ত্র ধারণে সক্ষম।
এই প্রসঙ্গে আরেকটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। আলখাওয়ারিজকে (খারিজীদের) কাফির বলে চিহ্নিত না করা সম্পর্কে আলিমদেরও সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত ছিল, যদিও প্রামাণিক হাদীসে এরূপ লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ও তদেরকে হত্যা করার অনুমতি রয়েছে। এমাম শাওকানী ‘নায়লুল আওতারে’ লিখেছেন, অধিকাংশ সুন্নী ফকীহ মনে করেন, কালিমা পাঠ ও ইসলামের মূল আহকাম মেনে চলায় খারিজীরা মুসলমান। তারা অন্য মুসলমানকে কাফির বলে অভিহিত করে, তারা নিজেরাই নিজেদের ভুল ব্যাখ্যার ফাঁদে পড়ে। তাদের পাপ ঐ ভুলেরই পরিণতি। আল-খিতাবী বলেন যে, যতোক্ষণ তারা ইসলামের মূলনীতিগুলো মেনে চলে ততোক্ষণ তাদের কাফির বলা ডাবে না। তাদের সাথে আন্তঃবিবাহ, খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদি করা যেতে পারে বলে আলিমরা একমত হয়েছেন।
ইয়াদ বলেন, মুতাকাল্লিমুনদের জন্যে একটি এটি অত্যন্ত জটিল বিষয় ছিল। ফকীহ আবদুল হক এমাম আবু মা’লীকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছিলেন। তিনি একজন কাফিরকে এসলামের মধ্যে অথবা একজন মুসলমানকে এর আওতা থেকে বহিষ্কার করার মতো জটিল ধর্মীয় বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে অস্বীকার করেন। কাজী আবু বকর আল-বাকিল্লানীও এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে অপারগতা প্রকাশ করেন বলে তিনি জানান। তবে তিনি বলেন, আল-খাওয়ারিজ প্রকাশ্য কুফরী করেনি কিন্তু কুফরীর মতো কথাবার্তা বলেছে। আল-গাযালী (র) তার আত-তাফরিকাহ বাইনাল ইমাম ওয়াল জান্দাকাহ গ্রন্থে লিখেছেন, “কাউকে কাফির চিহ্নিত করার ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক হতে হবে। একজন মুসলমানের রক্তপাতের চেয়ে এক হাজার কাফিরের জীবন বাঁচানো অপেক্ষাকৃত কত মারাত্মক ভুল।”
ইবনে বাত্তাল (র) বলেছেন, অধিকাংশ আলিম আল-খাওয়ারিজকে ইসলামের আওতার বাইরে রাখেননি। নাওরাওয়ানের খারিজীদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়ে আলী (রা) বলেছেন যে, তারা কুফরী এড়িয়ে গেছে। বাত্তাল তাদেরকে বুগাত বলে বিবেচনা করা যায় বলে মত প্রকাশ করেন। আলিমরা এ ব্যাপারে একমত যে, তাকফীর (কাউকে কাফির বলে চিহ্নিত করা) এমন একটি মারাত্মক বিষয় যা মারাত্মক পরিণাম ডেকে আনতে পারে।মুসলিম মনীষীরা মূল প্রামাণিক সূত্র থেকে বিভিন্ন বিষয় সিদ্ধান্তে নেয়ার নির্দিষ্ট নীতি ও পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন। এ থেকে উসুল আল-ফিকাহ বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। বিজ্ঞানের এই অতুলনীয় শাখা ইসলামের প্রামাণিক সূত্র থেকে আইন প্রণয়নের পদ্ধতিগত ভিত্তি নির্মাণ করেছে। এ জন্যে মুসলমানরা গর্ববোধ করতে পারে। এছাড়া উসুল থেকে কোনো নীতি সূত্র পাওয়া না গেলে উসুল আত-তাফসীর ও উসুল আল-হাদীসে তার সন্ধান পাওয়া যেতেপারে। শারীয়াহ সম্পর্কে গভীর জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্য ঈমান, হাদীসের ব্যাখ্যা ও আইন সংক্রান্ত অসংখ্য বই পুস্তকের সাহায্যও নেয়া যেতে পারে।
অতএব জ্ঞানের এসব সূত্রের বিদ্যমানতায় কুরআনের আয়াত ও হাদীসের মর্ম গভীরভাবে উপলদ্ধি করার ক্ষেত্রে কোনো অসুবিধে থাকতে পারে না। অগভীর ভাসাভাসা জ্ঞানের কোনো অবকাশ নেই। এই লক্ষ্যে নিম্মোক্ত বিষয়গুলো অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে:
প্রথম: ইসলামের সার্বিক সত্যের প্রেক্ষিতে সকল বিশেষ বিশেষ দিক বিবেচনা ব্যতিরেকে শারীয়াহ সম্পর্কে গভীর জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি পরিপক্ক হতে পারে না। কুরআনের একটি আয়াত অথবা একটি হাদীস অবশ্যই ব্যাখ্যা করতে হবে অন্য আরেকটি হাদীস হাদীস, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সুন্নাহ, সাহাবীদের জীবন ও উসূল আত-তাফরীরে আলোকে। এছাড়া সার্বিক প্রেক্ষাপট ও শারীয়াহর উদ্দেশ্যকেও সামনে রাখতে হবে। অন্যথায় উপলব্ধি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ভ্রান্তির ফলে শরীয়তে পরস্পর বিরোধীতার আপদ দেখা দেবে। এ কারণে ইমাম আশ-শাতিবি (র) ইজতিহাদের ক্ষেত্রে দু’টি শর্ত আরোপ করেছেন: (ক) সামগ্রিক চৈতন্যে শরীয়ত অনুধাবন ও (খ) সেই উপলব্ধির আলোকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা। এই শর্ত পূরণের একমাত্র উপায় হচ্ছে কুরআনের ও হাদীসের গভীর জ্ঞান এবং সেই সাথে কারণ, ঘটনাবলী, পরিবেশ, পরিস্থিতি এবং প্রতিটি আয়াত ও হাদীসের উদ্দেশ্যে সম্পর্কে সম্যক অবহিত হতে হবে। এছাড়া চিরন্তন অপরিবর্তনীয় এবং সাময়িক চাহিদা পূরণ, প্রচলিত প্রথা ও ঐতিহ্য, বিশেষ বিশেষ সময়ের ঘটনাবলী এবং পরিবর্তিত অবস্থায় এসবের পরিবর্তন ইত্যাদির রূপভেদ নির্ণয়ের ক্ষমতা থাকতে হবে।
একদিন আমি মহিলাদের ইসলামী পোশাক সম্পর্কে বক্তৃতা করছিলাম। একজন শ্রোতা বললেন, কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী হিযাবের সাথে একটি অতিরিক্ত বহিরাবরণ থাকতে হবে। আমি জবাব দিলাম, হিযাব নিজেই একটি উদ্দেশ্য নয়, বরং শরীরের শরীয়ত নিষিদ্ধ অংশগুলো শালীনভাবে আবৃত করার উপায় মাত্র এই সময় ও স্থানভেদে এর ধরন বিভিন্ন রকম হতে পারে। কিন্তু লোকটি অগ্নিশর্মা হয়ে চিৎকার করে বলল, কুরআন শরীফে পোশাক সুস্পষ্টত নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। এটা পরিবর্তনের অধিকার আমাদের নেই বলে সে কুরআনের এই আয়াতটি তিলাওয়াত করলো:
“হে নবী! আপনার স্ত্রীগণ, কন্যাগণ ও ঈমানদারদের নারীদের বলুন, যেন তারা তাদের চাদরের কিয়দাংশ নিজেদের উপর টেনে দেয়। এতে তাদেরকে চেনা সহজতর হবে; ফলে তাদের উত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।” (৩৩:৫৯)
আমি বললাম, কুরআনুল করীমে কখনো কখনো ওহী নাযিলের সমসাময়িক অবস্থার দিকে লক্ষ্য রেখে উপায় ও পদ্ধতি বাতলে দেয়া হয়েছে। এর চেয়ে উত্তম বা অনুরূপ অন্য কোনো উপায় উদ্ভাবিত হলে ঐটাই স্থায়ীভাবে মানতে হবে এমন ধরা বাঁধা তাৎপর্য ঐ আয়াতে নিহিত নেই। এর পক্ষে নিম্মোক্ত উদাহরণটিই যথেষ্ট: কুরআনুল করীম বলছে: “তোমরা তাদের মোকাবিলার জন্য যথাসাধ্য শক্তি ও অশ্ববাহিনী প্রস্তুত রাখবে। এতদ্বারা তোমরা সন্ত্রস্ত করবে আল্লাহর শত্রুকে, তোমাদের শত্রুকে এবং এতদ্ব্যতীত অন্যদেরকে, যাদেরকে তোমরা জান না, আল।রাহ জানেন।” (৮:৬০)
এই আয়াত নাযিলের সময় ঘোড়া ছিল যুদ্ধের সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যমগুলোর মধ্যে অন্যতম। তাহলে এখন কি মুসলমানরা ট্যাংক, জঙ্গী বিমান, বোমা ইত্যাদি ব্যবহার করতে পারবে না? এটা যদি ঠিক না হয় তাহলে এই আলোকে মুসলিম মহিলারাও শ্লীলতার উদ্দেশ্য সামনে রেখে যে কোনো বহিরাবরণ ব্যবহার করতে পারে।
আল-হাদীসকেও একইভাবে মূল্যায়ন করা যায়। আল-হাদীস ও শিক্ষায় জীবনের নানা ক্ষেত্রের প্রণালী-প্রক্রিয়া বিধৃত হয়েছে যার কতকাংশ আইন এবং অনেকাংশ আইন নয়; কিছু সাধারণ, কিছু নির্দিষ্ট, কিছু অপরিবর্তনীয়, কিছু পরিবতর্নীয়।পানাহার, পোশাক ইত্যাদি ব্যাপারে নির্দিষ্ট আইন আছে। আবার নির্দিষ্ট আইন নয় এমন সুন্নাহ ও রীতি-প্রথাও রয়েছে। যেমন- চামচের পরিবর্তে হাত দিয়ে খাওয়া বাধ্যতামূলক নয়। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সময়ে হাত দিয়ে খাওয়া আরবদের সাধারণ জীবনযাত্রার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল। এর অর্থ এই নয় যে, চামচ ব্যবহার হারাম। কিন্তু সোনা- রূপোর তৈজসপত্র সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। একইভাবে ডান হাত ব্যবহারের অভিন্ন প্রথা প্রবর্তন এর উদ্দেশ্য। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, “বিসমিল্লাহ বলো (খাওয়ার আগে) এবং ডান হাত দিয়ে খাও।” (অনুমোদিত হাদীস) আরেকটি হাদীসে তিনি বলেন, “তোমাদের বাম হাতে পানাহার করা উচিত নয়। কারণ শয়তান বাম হাতে পানাহার করে।” (মুসলিম)
রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সময় চালুনি সম্পর্কে কোনো ধারনা ছিল না। তাই বলে এটার ব্যবহার এখন বিদআত হতে পারে না।
অনেক তরূণ খাট ইজার বা ছওব পরিধানকে ইসলামের মৌলিক বিষয় মনে করে। তাদের প্রথম যুক্তি রাসূলুল্লাহ (সা) ও তাঁর সাহাবারা এটা পরিধান করেছিলেন। দ্বিতীয়ত হাদীসে গোড়ালির নিচে পর্যন্ত ইজার বা ছওব পরা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। হাদীসটি হচ্ছে: “গোড়ালির নিচে ইজার পরিধানকারী ব্যাক্তি দোযখে যাবে।” (বুখারী)
প্রথম যুক্তিটির ব্যাপারে বলা যায়, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সুন্নাহ সম্পর্কে আমরা যা জেনেছি তাতে দেখা যায় তিনি যখন যেমন পেয়েছেন তেমনিই পরেছেন। তাকে কোর্তা, ঢিলে জামা এবং এজারও পরতে দেখা গেছে। তিনি এয়েমেন ও পারস্য থেকে প্রাপ্ত (কিনারে সিল্কের নক্শা করা) কাপড়ও পরেছেন। পাগড়ি ছাড়া বা পাগড়[ইসহ টুপিও পরেছেন।
ইমাম ইবনূল কাইয়েম (র) তাঁর আল-হাদী আন-নববী বইয়ে লিখেছেন: পোশাক সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সর্বোত্তম রীতি তাই যা তিনি নিজে ব্যবহার করেছেন, করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং উৎসাহিত করেছেন।-তিনি উয়েমেনের পোশাক, সবুজ কাপড় চোপড়, জুব্বাহ, ফুলহাতা জামা এবং জুতা-স্যান্ডেলও পরেছেন। তিনি কখনো কখনো বাবরিও রেখেছেন।
তখন বস্ত্রকল অজ্ঞাত ছিল। ইয়েমেন, মিসর ও সিরিয়া থেকে কাপড় আমদানী করা হতো। এখন আমরা বিভিন্ন ধরনের অর্ন্তবাস ব্যবহার করি। তখন তা ছিল না। অতএব এসব নিয়ে অহেতুক শোরগোল কেন?
দ্বিতীয়: কুফফারের অনুকরণ সংক্রান্ত যুক্তি প্রশ্ন বলা যায়, আমাদেরকে আসলে কুফফারদের (অন্য ধর্মের অনুসারীদের) বৈশিষ্ট্য অনুসরণে নিষেধ করা হয়েছে; যেমন-ক্রস, ধর্মীয় পরিচ্ছদ, দর্মীয় আচার-সিরাত আল-মুসতাকিম মুখলিফাত আহলিল জাহীম” পুস্তকে এগুলোর বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। এখন একজন মুসলমান যদি ইচ্ছাকৃত কুফফারকে অনুসরণ করে তবে তা দোষনীয়। কিন্তু কেউ যদি অনিচ্ছাকৃতভাবে প্রয়োজনের তাকিদে করে তবে তা দোষনীয়। যেমন কোনো ফ্যক্টরী শ্রমিক বা ইঞ্জিনিয়ার কাজের সুবিধার্থে “ওভারঅল” পরলে দৌষের যথাসম্ভব নিজেস্ব বৈশিষ।ট্য ফুটিয়ে তোলা উচিত। সারকথা, খাটো ছওব পরা বাঞ্ছনীয়, কিন্তু ঔদ্ধত্যের পরিচায়ক না হলে লম্বা কাপড় পরা নিষিদ্ধ নয়।
উপরের উদাহরণগুলো নির্ভেজাল ব্যাক্তিগত ব্যাপার। অথচ আমরা বৃহত্তর জাতীয়, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক জটিল বিষয়গোলো নিয়ে এতো মাথা ঘামাই না যদিও তা গোটা উম্মাকে হুমকির মুখে ঠেলে দৈয়া এসব সমস্যা সমাধানে বরং আমাদেরকে ইসলামী আইনের গভিরে প্রবেশ করা উচিত।
আমাদের এটা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, এখন আমরা এক জটিলতম জগতে বাস করছি। নানা মত ও আদর্শের নজিরবীহিন প্রসারের ফলে পৃথিবী ছোট হয়ে এসেছে। সমাজে দুর্বল-শক্তিশালী, মহিলা-পুরুষ, সৎ ও সীমালংঘকারী ইত্যাদি রয়েছে। অতএব ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা পুনরুজ্জাঈবনের আন্দলনের প্রতি মানুষকে আহবান জানানো এবং কোনো বিষয়ে ফতোয়া দেয়ার সময় এই জটিল প্রেক্ষাপট বিবেচনা করতে হবে। আল্লাহর রেজামন্দি প্রত্যাশী একজন মুসলমান ব্যক্তি জীবনে চরমপন্থী মত পোষণ কিংবা কঠোর নিয়মশৃখলার মনে চলতে পারে। গান-ব্দ্য, নাটক এসবের স্থান তার জীবন নেই। কিন্তু কোনো আধুনিক রাষ্ট্র টিভি, রেডিও, আলোকচিত্র, সংবাদপত্র বা সংবাদ মাধ্যম ছাড়া চলতে পারে না। ইমিগ্রেশন, পাসপোর্ট, ট্রিফিক, শিক্ষা ও আইন শৃংখলার ক্ষেত্রে ছবি এখন অপরিহার্য। অপরাধ ও জালিয়াতি প্রতিরোধে এর ব্যবহার এখন ব্যাপক ও অত্যাবশ্যক। অতএব আধুনিক কোনো রাষ্ট্র ও সমাজ কি টিভির গুরুত্ব অস্বীকার করতে পারে? অথচ ফটোভিত্তিক বলে অনেকে এটাকে হারাম বলে মনে করেন।
সংক্ষেপে আমি যা বলতে চাই, নিছক ব্যক্তি জীবনে কড়াকড়ি সহনীয়; কিন্তু সমাজ বা রাষ্ট্রের উপর তা চাপিয়ে দেয়াএ চিন্তা অবাস্তব। একানে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাদীসটি আবার স্মতূব্য: “যে নামাযের ইমামতি করে তার উচিত নামায সংক্ষিপ্ত করা। কেননা জামাতে দুর্বল, বৃদ্ধ এবং ব্যস্ত লোকও থাকে।” (বুখারী)
একটি মারাত্মক সমস্যা হচ্ছে, আমাদের মধ্যে অনেকে এটা স্বীকার করতে চান না যে, শরীয়তের সকল আহ্কাম সমভাবে গুরুত্বপূর্ণ নয়। আহ্কামের বিভিন্ন ব্যাখ্যা থাকতে পারে এটাও তারা মানতে চান না। প্রথা, আচার-আচরণ ও দৈনন্দিন লেনদেনের ক্ষেত্রে অনেক বিষয় আনুমানিক সিদ্ধান্তের উপর নির্ভরশীল। এগুলো ইজতিহাদ সাপেক্ষ এবং স?ঠিক ইজতিহাদ থেকে উৎসারিত সিদ্ধান্তবলীতে মতানৈক্য ক্ষতিকর নয়, বরং এটি শরীয়তে নমনীয়ত ও ফিকাহর ব্যাপকতার প্রমাণ এবং উম্মার জন্যে আশীর্বাদ। এসব বিষয় সাহাবায়ে কিরাম (রা) এবং তাদের উত্তরর্সরীদের মধ্যেও মতভেদ ছিল। কিন্তু এগুলো কখনোই তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে পারেনি। অন্যদিকে ঈমান ও ইবাদত সম্পর্কিত আহকাম কুরআন ও সুন্নাহতে সুস্পষ্ট ও সুনির্ধারিত। এটা মুসলিম উম্মার মানসিক ও আচরণগত ঐক্যের প্রতীক। এগুলো থেকে বিচ্যূতি শুধু পাপ নয়, একজনকে কুফরীর দিকেও ঠেলে দিতে পারে। এছাড়া আরো কিছু আহকাম আছে যেগুলো প্রত্যাখ্যান করা আল্লাহ ও রাসূলকে অস্বীকার করার নামান্তর। পক্ষান্তের এমন সব বিষয় আছে যেগুলো ব্যাখ্যা নিয়ে ফকীহরা মতভেদ করেছেন। যেমন, কেউ বাধ্য হয়ে একজন মুসলমানকে হত্যা করলে, হত্যাকারী, না যে হত্যা করালো, কে শাস্তি পাবে? না-কি উভয়ে শাস্তি ভোগ করবে? এই জটিল প্রশ্নের বিভিন্ন মিজহাবের ফীকহ বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কেবল ইমাম আহমদ (র)-এর হাম্বলী মাজহাবেই এ ব্যাপারে এতো মতভেদ রয়েছে যে, তারা এ নিয়ে ১২ খন্ডের বই লিখেছেন। বইটির নাম: আল-ইনসাফ ফীর রাজিহ মিনাল ইখতিলাফ।
এই প্রেক্ষিতে মুসলিম তরুণদেরকে মতানৈক্য ও মতৈক্যের বিষয়গুলো এবং মতানৈক্য নিরসনের মনদন্ড সম্পর্কে অবহিত হতে হবে। এই লক্ষ্যে আমাদের আলিম ও উলামার কাছ থেকে প্রাপ্ত মতভেদ নীতি বা আদাব আল-ইখতিলাফের সাথে পরিচিত হওয়া আবশ্যক। তাহলে আমরা বিভিন্ন ধর্মীয় বিষয়ে উদার ও পরমতসহিষ্ণু হওয়ার শিক্ষা লঅভ করতে পারব। ভ্রাতৃত্ব বজায় রেখেও আমরা কিভাবে মতভেদ করতে পারি? প্রথমেই আমাদের উপলব্ধি করতে হবে, প্রান্তিক বিষয়ে মতনৈক্য স্বাভাবিক। সুস্পষ্ট আহকাম ও অস্পষ্ট আহকাম সৃষ্টির পেছনেও ঐশী প্রজ্ঞা রয়েছে। অস্পষ্ট আহকাম ও বিভিন্নমুখী হওয়া সত্ত্বেও এর মধ্যে ভ্রাতৃত্বসুলভ মতভেদেরও সম্ভ।আবনা থাকে। এটাও আল্লাহ্ তায়ালার আর্শীবাদ, বিশেষ করে সেই সব আলিমের উপর যারা মজহাব নির্বিশেষে একটি বিষয়ের সকল দিক বিচার বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম। এরূপ বিশিষ্ট আয়েম্মোর সারিতে যারা রয়েছেন তাঁদের কয়েকজনের নাম উল্লেখযোগ্য: উবনে দাকীক আল ঈদ, ইবনে তাইমিয়া, ইবনুল কাইয়েম, ইবনে কাছীর, ইবনে হাজার আল আছকালানী, আল দাহলাবী, আশ-শাওকানী, আল-সানানী (র) বলতেন: “আমি কখনোই কামনা করিনি যে, সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে মতনৈক্য না থাক। তাদের মতনৈক্য রহমতস্বরূপ।”
এমনকি রাসূলুল্লাহ্ (সা) -এর জীবদ্দশায়ও একটি বিষয়ের বিভিন্ন ব্যাখ্যা পাওয়া যেতো। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এগুলো অনুমোদন করতেন এবং তিনি ব্যক্তি বিশেষ বা গ্রুপকে দোষী বলে চিহ্নিত করতেন না। জঙ্গে আহযাবের পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবীদের উদ্দেশ্যে বললেন: “যে ব্যক্তি আল্লাহ ও কিয়ামত দিবসে বিশ্বাস করে সে যেন বানু কুরাইজায় (বসতা) না পৌঁছা পর্যন্ত সালাতুল আসর আদায় না করে।” (বুখারী ও মুসলিম) কতিপয় সাহাবী এটাকে অসম্ভব মনে করে গন্তব্যে পৌঁছার আগেই সালাত আদায় করে নিলেন। অন্যরা অর্থাৎ আক্ষরিক অর্থ গ্রহণকারীরা বানু কুরাইজার পৌঁছে নামায পড়লেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে এটা জানানো হল, তিনি উভয় পক্ষের কাজ অনুমোদন করলেন যদিও একপক্ষ ভুল করেছিল। এ থেকে আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারি, নিরেট প্রমাণের ভিত্তিতে প্রণীত ব্যাখ্যাকেই মেনে চললে তাতে পাপ হওয়ার কোনো আশঙ্কা নেই।
দুভার্গজনকভাবে আজকার একদল লোক আছেন যারা দাবী করেন তারাই সকল সত্যের আধার এবং সব প্রশ্নের জবাব তাদের কাছেই আছে এবং অন্যের উপর তা চাপি’য়ে দদিতে চান। তারা মনে করে তারা সকল মাযহাব ও মতভেদ নির্মূল করে এক আঘাতেই সকলকে একই প্লাটফর্মে হাযির করতে সক্ষম। তারা এ কথা বেমালুম ভুলে যান যে তাদের সিদ্ধান্তটাও অনুমান নির্ভর এবং তা ভুল বা শুদ্ধ উভয়ই হতে পারে। মোটকথা কোনো মানুষ অথবা কোনো আলিম অভ্রান্ত নন। একমাত্র নিশ্চিত ব্যাপার হচ্ছে, তার ইজতিহাদের জন্যে তিনি পুরস্কার পাবেন ভুল বা শুদ্ধ যাই হোক। অবশ্য তার নিয়ত সৎ থাকতে হবে। সুতরাং উপরোল্লিখিত ব্যক্তিরা একটা অতিরিক্ত মাহযাব সৃষ্টি ছাড়া আর কিছুই আশা করত পারেন না! এটা অদ্ভুত যে, তারা মাহযাবের অনুসৃতি অনুমোদন করেন না, কিন্তু অন্যকে নিজেদের নতুন মাহযাব অনুসরণে প্রলুবাধ করেন। তারা চান তাদের সৃষ্ট ‘একমাত্র’ মাহযাব সকলেই মেনে নিক। একবার এই ‘একমাত্র’ মাহযাবের একজন অনুসারী আমাকে জিজ্ঞেস করলেন: কেন সকল মুসলমান একটি মাত্র ফিকহী মতের অনুসারী হতে পারেন না? আমি জবাবে বললাম যে, মৌলসূত্রের ভিত্তিতে সকলের ঐকমত্য চাই। তা হতে হবে প্রামাণিক, অভিন্ন ও নির্বিরোধ এবং সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য। এর বিরোধিতায় আর কোনো মৌলসূত্র উথ্থাপিত হতে পারবে না এবং পূর্বোল্লিখিত তিনটি বিষয়ে সকল আয়েম্মায়ে হাদীসের মতৈক্য থাকতে হবে। সংক্ষেপে, এই বিষয়ে ইমাম ইবনে তাইমিয়া (র)-এর “রাফআল মালাম আনিল আয়েম্মাইল আলাম,শাহ ওয়ালীউল্লঅহ দেহলভীর হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ ও আল-ইনসাফ ফী আসবাবিল ইখতিলাফ এবং শেখ আলী আল-খলীফার আসবাব ইখতিলাফীল ফুকাহা” গ্রন্থে যেসব শর্তের উল্লেখ করা হয়েছে তা পূরণ করতে হবে। এখন আসুন আমরা নিচের হাদীসগুলো পর্যালোচনা করি:
১. যে নারী সোনার হার পরবে তাকে কিয়াতমের দিনে অনুরূপ একটি আগুনের তৈরি হার পরানো হবে এবং যে নারী সোনার দুল পরবে তাকে কিয়ামতের দিন অনুরূপ একটি আগুনের তৈরি দুল পরানো হবে। (আবু দাউদ, নাসায়ী)
২. কেউ যদি তার প্রিয়জনকে কিয়ামতের দিন আগুনের দুল পরাতে চায় তবে সে যেন তাকে সোনার দুল পরেত দেয় এবং কেউ যদি তার প্রিয়জনকে কিয়ামতের দিন আগুনের বালা পরাতে চায় সে যেন তাকে সোনার বালা পরতে দেয়। কিন্তু তোমারা পছন্দ মতো রূপা ব্যবহার করতে পারো। (আবু দাউদ)
৩.ছওবান (রা) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর কন্যা ফাতিমাকে (রা) সোনার চেন পরার জন্যে হুঁশিয়ার করে দিয়েছিলেন। এতে সাড়া দিয়ে তিনি সেটা বিক্রি করে একটি গোলাম খরিদ করলেন এবং তাকে আযাদ করে দিলেন। যখন রাসূলুল্লাহ (সা)-কে এ কথা জানানো হলো তখন তিনি বললেন, আলহামদু লিল্লাহ! তিনি ফাতিমাকে আগুন থেকে বাঁচিয়ে নিলেন।
ফকীহরা এসব হাদীস সম্পর্কে বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন: কেউ কেউ এগুলোর এনসান (হাদীসের বর্ণনা সূত্র) দূর্বল বলে প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং নিষিদ্ধ করার জন্যে অপর্যাপ্ত বিবেচনা করেছেন। কেউ কেউ ইসনাদকে সঠিক বললেও অন্য সূত্র থেকে প্রমাণ করেছেন যে, মেয়েরা সোনার অলংকার ব্যবহার করতে পারে। আর-বায়হাকী ও অনান্য ফকীহ এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন বলে লিখেছেন এবং একে স্বীকৃত প্রচলন বলে ফিকায় মেনে নেয়া হয়েছে।
অন্য ফকীহরা অন্য হাদীসের ভিত্তিতে, যারা মজুদ সোনার যাকাত আদায় করেননি, তাদের ক্ষেত্রে এই হাদীস প্রযোজ্য বলে রায় দিয়েছেন। এই অন্য হাদীসগুলো আবার সমালোচনার উর্ধ্ব নয়। আবার, মহিলাদের গহণার যাকাত সম্পর্কেও বিভিন্ন মাযহাবে মতভেদ রয়েছে।
কেউ কেউ আবার যুক্তি দেখিয়েছেন, যেসব মহিলা অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে অহংকারবশত সোনার অলঙ্কার পরে এই হাদীসে তাদেরকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। আন নাসাঈ এই বিষয়ের সাথে সংগতিপূর্ণ কতিপয় হাদীস উল্লেখ করে “বাবুল কারাহিয়াহ লি নিসা এজার আলহালি জাহাব” শীষর্ক পস্তুক রচনা করেছেন। অনান্য ফকীহ বলেছেন, অহংকারবশত অতিরিক্ত সোনা ব্যবহার প্রশ্নের হাদীস জড়িত।
আধুনিক কালে শেখ নাসিরুদ্দীন আর-আলবানী (র) গত ১৪শত বছরেএ সকল মাযহাবের রায় বাতিল করে দিয়ে বলেছেন, হাদীসগুলোর ইসনাদ শুধু প্রমাণিকই নয়, এগুলো অন্য হাদীস দ্বারা বাতিলও হয়নি। সুতরাং গলার হার ও কানের দুল পরা নিষিদ্দ।
অতএব মতনৈক্যের যে দুর্বার স্রোত এগিয়ে চলছে তা কি বালির বাধ দিয়ে রুখা সম্ভব? প্রশ্নের জবাব অতি পরিষ্কার: “মতাভেদের অসংখ্য স্রোতধারা প্রবাহিত হতেই থাকবে, কিন্তু তা আমাদেরকে নিসজ্জিত করতে পারেবে না ইনশাআল্লাহ।” আল্লাহ্ তায়ালা বলেন: “প্রত্যেকেরই একটা দিক আছে, যার দিকে সে মুখ করে দাঁড়ায়।” (২:১৪৮)
এ প্রসঙ্গে আমি বলতে চাই আধুনিক কালে একজন মাত্র ধর্মীয় নেতা মতভেদের নীতি ও তাৎপর্য গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি ইমাম হাসান আল-বান্না (র)। মুসলিম উম্মাহর সংগতি লক্ষ্যে নিবেদিত হয়েও তিনি তার অনুসারীদের এর নূন্যতম মর্ম উপলব্ধি করাতে পেরেছিলৈন এবং ইসলামী নীতিমালার ভিত্তিতে ঐক্যমত সৃষ্টি তাদেরকে এক প্লাটফর্মে সমবেত করার নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তিনি মতভেদের অনিবার্যতা সম্পর্কে স্থির নিশ্চিত হয়েছিলেন। তার বিখ্যাত উসুল আল-ইশরুন গ্রন্থ থেকে এটা সুস্পষ্ট হয়। এ বিষয়টি তিনি দক্ষতার সাথে তার বিভিন্ন বাণীতে তুলে ধরেছেন। ‘আমাদের দাওয়াত’ শীষর্ক বাণীতে তিনি বলেন যে, তার আহবান সর্বসাধারণের প্রতি, কোনো বিশেষ গ্রুপের প্রতি নয় এবং কোনো বিশেষ চিন্তাধারার প্রতিও নয়। দ্বীনের প্রকৃত মর্ম উপলব্ধি করাই আমাদের কাম্যঅ এজন্যে বৃহত্তর কল্যাণে সকল প্রচেষ্টা সম্মিলিত খাতে প্রবাহিত করাই আমাদের লক্ষ্য। আমরা মতৈক্য চাই, খামখেয়ালী নয়। কারণ সকল দুর্ভাগ্যের জন্যে দায়ী ভ্রান্তিপূর্ণ মতভেদ। আমরা বিশ্বাস করি বিজয় অর্জনের জন্যে ভালবাসা একটি বড় উপাদান অতএব ব্যার্থতার দিকে টেনে নিয়ে যেতে পারে এমন বিষয় পরিহার করাই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু এ সত্ত্বেও তিনি লিখেছেন:
“নানা কারণে ছোটখাট ধর্মীয় বিষয়ে মতভেদ অনিবার্য। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারনগুলো হচ্ছে বুদ্ধিবৃত্তির মাত্রা ও জ্হানের গভীরতার তারতম্য, বহুবিদ বাস্তব ঘটনা ও থথ্যের পারস্পারিক সম্পর্কে এবং ভাষায় অন্তর্নিহিত দ্ব্যর্থতা। এসব কারণে মূলসূত্রের ব্যাখ্যার বিভিন্নতার দরুন মতভেদের উদ্ভব অপরিহার্য।
ইসলামী বিশ্বের কোনো অংশে জ্ঞানের উৎসের প্রাচুর্য আবার অনান্য জায়গায় দুষ্পাপ্যতাও একটি বড় কারণ। এমাম মালিক (র) আবু জাফরকে (র) বলেন, “রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাহাবীরা বিভিন্ন দূরবর্তী অঞ্চলে ছড়িয়েপড়েছিলেন, প্রত্যেকের কাছে জ্হান সঞ্চিত ছিল। তুমি যদি একটিমত অনুসরণে জবরদস্তি করো তাহলে ফিতনা সৃষ্টি করবে।”
পরিবেশগত পার্থকও রয়েছে। ইমাম শাফিঈ (র) ইরাক ও মিসরের বিরাজমান অবস্থার প্রেক্ষিতে ভিন্ন ভিন্ন ফতোয়া দিতেন। উভয় ক্ষেত্রে তিনি যা সত্য বলে রা’বীর প্রতি ইমামের দৃষ্টিভঙ্গি মতপার্থক্যের আরেকটি কারণ। একজন রা’বীকে একজন এমাম নির্ভরযোগ্য বিবেচনা করেন, আরেকজন তাতে সংশয় প্রকাশ করেন।
এসব কারণে আমরা বিশ্বাস করি, ধর্মীয় গৌণ বিষয়ে সর্বসম্মত মত অসম্ভব নয়, দ্বীনের প্রকৃতির সাথে অসংতিপূর্ণ। কেননা এরূপ দাবী কঠোরতা ও বাড়াবাড়ি জন্ম দেবে। আর এটা ইসলামের সরলতা, নমনীয়তা ও উদারতার পরিপন্থী। নিঃসন্দেহে এই মূল্যবোধগুলোর কারণেই ইসলাম যুগের দাবী মেটাতে সক্ষম।
অধিকন্তু, যেহেতুঋ আমরা সকলে ইসলামের সুবিস্তৃত কাঠিমোর আওতাধীন তাই গৌণ বিষয়ে মতভেদ আমাদের পারস্পারিক ভালবাসা ও সহযোগিতাকে ক্ষুণ্ণ করতে পারে না। আমরা যদি মুসলমান হই তাহলে আমরা কি মুসলমান ভাইদের পোষণ করে যাওয়ার সম্ভাব্য প্রীতিপূর্ণ পরিবেশ গড়তে পারি না? অন্তত এ প্রশ্নে তো একমত হতে পারি।
রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাহাবীরা ফতোয়ায় মতভেদ পোষণ করেছেন কিন্তু তা অনৈক্য সৃষ্টি করেনি। সালাহ ও বনু কুরাইজার ঘটনাটি এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। তারা আমাদের চেয়ে ভালভাবে জানা সত্ত্বেও যদি মতভেদ করে থাকেন তাহলে এটা কি অবাঞ্ছিত নয় যে, আমরা তুচ্ছ ব্যাপারে বিদ্বেষবশত মতনৈক্যে লিপ্ত হই? যদি আমাদের ইমামগণ বিভিন্ন বিষয়ে মতদ্বৈততা পোষণ করেন তাহলে আমাদেরও তা হতে পারে। যদি প্রাত্যহিক আযানের মতো প্রতিষ্ঠিত গৌণ বিষয়ে মতবিরোধ থাকতে পারে তাহলে অন্যান্য জটিল বিষয়ের কি দৃশ্য হবে?
আমাদেরকে এটাও স্মরণ রাখতে হয় যে, খিলাফত আমলে বিরোধীয় বিষয়গুলো খলিফার কাছে পেশ করা হতো। এখন যেহেতু খলীফা নেই সেহেতু এমন নির্ভরযোগ্য সূত্র বা ব্যক্তিত্ব খুঁজতে হবে যেন সেখানে বিরোধপূর্ণ বিষয়গুলো সমাধান করা যায়; নতুবা মতবিরোধ আরেকটি মতবিরোধের জন্ম দবে। পরিশেষে,আমাদের ভ্রাতাগণ এসব বিষয়ে পূর্ণ সচেতন এবং তাদের মধ্যে সহিষ্ণুতা ও উদারতা থাকা আবশ্যক। তারা বিশ্বাস করেন প্রতিটি গ্রুপের দাওয়াতের মধ্যে কিছু সত্য, কিছু মিথ্যা উপাদান থাকতে পারে। তারা সতর্ক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর সত্যকে গ্রহণ করেন এবং যারা ভুল উপলব্ধি করেন, তাহলে খুব ভালো, আর যদি না করেন তবুও তাঁরা আমেদর মুসলিম ভাই। আমরা আল্লাহর কাছে সঠিক পথের দিশা চাই!”
ফিকাহর মতভেদ সংক্রান্ত একটি ঘটনার উল্লেখ করতে চাই। রমযান মাসে একদিন তিনি মিসরের একটি ছোট গ্রামে বক্তৃতার দাওয়াত পান। সেকানে দু’দল লোক তারাবীর নামাযের সংখ্যা নিয়ে বাকবিতণ্ডা করছিল। একদল বলল, উমর ইবনে খাত্তাব (রা)-এর দৃষ্টান্ত অনুযায়ী ২০ রাকাত। আরেক দল ৮ রাকাতের উপর জোর দিচ্ছিল। তাদের যুক্তি ছিল রাসূলুল্লাহ (সা) কখনো আট রাকাতের বেশি তারাবীহ পড়েননি। উভয় পক্ষ একে অপরকে বিদাতের অভিযোগে অভিযুক্ত করল। পরিস্থিতি এক পর্যায়ে হাতাহাতির উপক্রম হলো। তারা আল-বান্না (র)-এর কাছে বিষয়টি পেশ করল। তিনি প্রথম প্রশ্ন করলেন: তারাবীহ কী ধরনের ধর্মীয় অনুষ্ঠান? জবাব এলো: সুন্নাত, পালন করলে সওয়াব, না করলে গুনাহ। অতঃপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন: মুসলিম ভ্রাতৃত্ব সম্পর্কে কী মত? তারা জবাব দিল: বাধ্যতামূলক এবং ঈমানের অন্যতম মৌলিক বিষয়। কখন আল-বান্না (র) বললেন: তাহলে শরীয়তের দ্রষ্টিতে ফরয অথবা সুন্নতের মধ্যে কোন্টি পরিত্যাগ করা যুক্তিযুক্ত? অতঃপর তিনি বললেন: আপনারা যদি ভ্রাতৃত্ব ও ঐক্য চান তাহলে প্রতিটি বাড়িতে গিয়ে নিজেদের বিশ্বাস মোতাবেক তারাবীহর নামায পড়ুন। তর্ক করার চেয়ে এটাই উত্তম।
ঘটনাটি আমি কিছু লোকের কাছে বর্ণনা করলে তারা বললেন, আল-বান্নার পদক্ষেপ সত্য এড়িয়ে যাওয়ার শামিল। তিনি সুন্নাত ও বিদাতের পার্থক্য নিরূপণ করেননি। আমি বললাম, এ বিষয়ে মত বিরোধের অবকাশ আছে। আমি নিজে যদিও তারাবীহর নামায আট রাকাত পড়ি, কিন্তু যারা বিশ রাকাত পড়ে তাদেরকে বিদাতীর দায়ে অভিযুক্ত করি না। তারা অনমনীয়তা ব্যক্ত করে বলল, এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দেয়া মুসলমানদের কর্তব্য। আমি যুক্তি দেখালাম, এটা হালাল ও হারামের ব্যাপারে সত্য; কিন্তু ফিকহী মাসলার ক্ষেত্রে নয়। সেখানে বিভিন্ন বিষয়ে মতভেদ আছে, অতএব প্রত্যেক পছন্দ অনুযায়ী একটি মত বেছে নিতে পারেন, কিন্তু এ ব্যাপারে গোঁড়ামি অনাবশ্যক।
অনেক বিজ্ঞ আলিম এটি স্বীকার করেছেন। হাম্বালী কিতাব ‘শারহে গায়াত আল-মুনতাহা’য় বলা হয়েছে:
কেউ যখন ইজতিহাদী সিদ্ধান্ত নাকচ করে তখন সে মুজতাহিদুনের মর্যাদা সম্পর্কে অজ্ঞতাবশত এরূপ করে, যাদেরকে আল্লাহ্ ভুল বা শুদ্ধ পরিশ্রম সাপেক্ষ সিদ্ধান্তের জন্যে পুরস্কৃত করবেন। তাদেরকে অনুসরণ গুণাহ হবে না। কেনা তারা যে ইজতিহাদে পৌঁছেছেন তা আল্লাহ্র নির্ধারিত পথ ধরেই এগিয়েছে; ফলে তা শরীয়তের অংশ হয়ে যায়। একটি উদাহরণ, প্রয়োজনে মৃত প্রাণীর গোশত খাওয়ার অনুমতি আছে, কিন্তু ইচ্ছাকৃত খাওয়া নিষিদ্ধ। দুটোই সুপ্রতিষ্ঠিত ফিকহী সিদ্ধান্ত।
ইমাম ইবনে তাইমিয়া (র) তাঁর ‘আল-ফাতাওয়াল মিসরীয়া’ বইয়ে বলেছেন, ঐক্যের কথা বিবেচনা করাই সঠিক পথ। অবশ্য সম্প্রতীতি ও সখ্যতা সৃষ্টির লক্ষ্যে পছন্দনীয় জিনিস পরিহার করাও সংগত। যেমন রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত ইবরাহীম (আ)-এর স্থাপিত ভিত্তির উপর কা’বা নির্মাণ পরিত্যাগ করেছিলেন*। ইমাম আহমদ (র)-এর মতো ইমামগণ ঐক্য রক্ষার স্বার্থে পছন্দনীয় বিষয় পরিহার করে মতৈক্যের বিষয় মেনে নেয়ার পক্ষপাতী।
ইবনে তাইমিয়া ৯র) কা’বা নির্মাণ সংক্রান্ত নিম্মোক্ত হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত আয়েশা (রা)-কে বলেন: তোমাদের জনসাধারণ সম্প্রতি যদি জিহিলিয়ার মধ্রে না থাকতো তআহলে আমি (হযরত) ইবারাহীম (আ)-এর ভিত্তির উপর কা’বা পুনঃনির্মাণ করতাম। ইবনুল কাইয়েম সালাতুল ফজরে কুনুতের বিষয়টিও তুলেছেন। কেউ এটাকে বিদাত বলেন আর কেউ এটা দুর্দিনে আমল করার পক্ষে। তিনি তাঁর বই ‘যাদুল মাদে’ বলেছেন, আপকালে এটা আমল করা রাসূলের সুন্নাত। হাদীস বিশারদরাও এটা সুন্নাত জেনে আমল করেছেন; আর যারা এটাকে রাসূলের সুন্নাত বলে জানতে পারেননি তারা এটাকে আমল করেননি। ইবনুল কাইয়েম লিখেছেন: “নামাযে রুকু থেকে ওঠার পর আল্লাহর রহমত কামনা ও তাঁর শুকরিয়া আদায়ের উপযুক্ত মুহূর্ত।”
রাসূলুল্লাহ (সা) এই অবস্থায় দু’টি কাজেই করেছেন। এ সময় ইমামের সশব্দে দোয়া পাঠ গ্রহণযোগ্য যাতে মোক্তাদিরা শুনতে পায়। উমর ইবনে খাত্তাব (রা) ও ইবনে আব্বাস (রা) ও এরূপ করতেন যাতে মানুষ সুন্নাহ জানতে পারে। উমর ইবনে খাত্তাব (রা) শব্দে সূরা ফাতিহা তিলাওয়াত করতেন এবং ইবনে আব্বাস (রা) জানাযার নামাযেও এরূপ করতেন। এগুলো গ্রহণযোগ্য মতভেদ সাপেক্ষ কাজ। যারা এরূপ করেন বা যারা করেন না কেউই দোষণীয় নন। যেমন নামাযে হাত তোলা, কিরান ও তামাত্তুর বিভিন্ন প্রক্রিয়া।
আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে রাসূলের সুন্নাত তুলে ধরা। কোন্টি জায়েয, কোন্টি নাজায়েয তা চিহ্নিত করার চেষ্টা আমি করিনি, বরং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সর্বোৎকৃষ্ট সুন্নাত তুলে ধরাই আমার উদ্দেশ্যঅ আমরা যদি বলি রাসূলুল্লাহ (সা)-নেই, তার অর্থ এই নয় যে, তিনি অন্যকে ও ব্যাপারে নিয়মিত করতে বলেছেন কিংবা কেউ পালন করলে তা রিদ্দাহর পর্যায়ভুক্ত হবে।
এক মাযহাবের অনুসারী অন্য মাযহাবের ইমামের পেছনে নামাযও আদায় করতে পারে; যদিও ঐ মুক্তাদি মনে করে যে, এতে তার মাযহাবে তা সিদ্ধ। এবনে তাইমিয়াহ (র) ‘আল-ফাওয়াকিহুল আদিদাহ’ পুস্তকে লিখেছেন: সাহাবায়ে কিরাম, তাবিঈন এবং চার ইমামের রীতি অনুসারে পরস্পরের পেছনে নামায পড়া সিদ্ধ বলে মুসলমানরা সর্বসম্মত। যে এটাকে অগ্রাহ করে সে বিপথে চালিত মুবতাদী এবং কুরআন ও সুন্নাহর শিক্ষা ও সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত থেকে বিছু্যত হয়।
কোনো কোনো সাহাবী ও তাবিঈন জোরে বাসমালাহ উচ্চারণ করেছেন, কিন্তু অন্যরা করেননি, এতদসত্ত্বেও তারা পরস্পরের পেছনে নামায আদায় করে?ছেন। আবু হানিফা (র) ও তার অনুসারীরাও তাই করেছেন। শাফিঈরা মদীনায় মালিকীদের পেছনে নামায পড়তেছিলেন। কারণ, ইমাম মালিক (র) ফতোয়া দিয়েছিলেন এই অবস্থায় নতুন করে অযু করার দররকার নেই।
অবশ্য ইমাম আহমদ আবনে হাম্বল (র) শরীর বা নাক থেকে রক্ষক্ষরণহলে অবশ্যই গোসর করতে হবে বলে মত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু কোন মুসল্লী যদি ইমামের শরীর থেকে রক্তক্ষরণ হতে দেখে তাহলে তার পেছনে সে নামায গড়ে যাবে কিনা এ প্রশ্নে ইমাম হাম্বাল (র) বলেন: “সাঈদ আবনে মুসাইয়াবের ও মালিকের (র) পেছনে নামায না পড়া অচিন্ত্যনীয়। অতঃপর তিনি দু’টো বিবেচ্য বিষয়ের উপর আলোকপাত করেছেন:
(ক) ইমামের কোনো আচরণ সালাতকে বাতিল করলেও তা যদি মোক্তাদির দৃষ্টি এড়ায় তাহলে মোক্তাদিকে নামায চালিয়ে যেতে হবে। এ ব্যাপারে পূর্ববর্তী ওলামা ও চার ইমাম একমত। (খ) কিন্তু ইমাম নাপাক হতে পারেন এমন কিছু যদি করেন আর সে ব্যাপারে মোক্তাদি যদি নিশ্চিত হয় তবে সে তার মর্জি মাফিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে। কেননা এ ব্যাপারে ব্যাপক মোনৈক্য রয়েছে। আমাদের পূর্ববর্তী বুযর্গদের মতে এরূপ ইমামের পেছনে নামায পড়া জায়েয। মালিকী মাযহাবও তাই মনে করে; কিন্তু শাফিঈ ও আবু হানিফা (র) ভিন্ন মত পোষণ করেন। আহমদের বিভিন্ন বক্তব্য থেকে এই মতের প্রতিই সমর্থন পাওয়া যায়। (আল ফাওয়াকিহ আলাআদিদা; কারাজাতি, ফতোয়া মুয়াসিরাহ।)
২. জ্ঞান, মূল্যবোধ ও কর্ম
শরীয়তী কাজ ও কর্তব্যের মূল্য উপলব্ধিতে ফিকাহর জ্ঞান সহায়ক ভূমিকা পালন করে। আর আদেশ ও নিষেধের মানদন্ডে এসব কাজ ও কর্তব্যের সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এই জ্হান বিবিধ ও সাদৃশ্যের মধ্যেকার বিভ্রান্তি প্রতিরোধ করে। জীবনের ওপর ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রভাবের আলোকে ইসলাম প্রতিটি কর্মের মূল্যমান নির্ধারণ করে দিয়েছে।
মুস্তাহাব (প্রশংসনীয়) কাজগুলো না করলে শাস্তি নেই, কিন্তু করলে পুরস্কার আছে। আবার এমন বিষয় আছে যা রাসূলুল্লাহ (সা) সর্বদা করেছেন, পরিহার করেননি; কিন্তু অন্যকে করার জন্যে সুস্পষ্ট আদেশ দেননি। এগুলো যে বাধ্যতামূলক নয় তা প্রমাণ করার সাহাবায়ে কিরাম এসব কাজের কিছু কিছু করেননি। মাযহাবগুলোর মত অনুযায়ী মুস্তাহাবের আদেশ আছে; কিন্তু সুস্পষ্টভাবে নয়। ফরয দ্বর্থহীনভাবে বাধ্যতামূলক, করলে সওয়াব, উপেক্ষা করলে গুনাহ। আর পালন না করলে ফিস্ক, পাপকার্য। আর বিশ্বাস না করলে কুফরী। ফরয দু’ভাগে বিভক্ত। ফরযে কিফায়াহ (সমষ্টিক কর্তব্য) ও ফরযে আইন (ব্যাক্তিগত কর্তব্য)। ব্যাক্তিগত কর্তব্য প্রত্যেক মুসলমানকে পালন করতে হবে। আর সমষ্টিক কর্তব্য কেউ করলেই চলবে, অন্যরা না করলে গুনাহ নেই। ব্যাক্তিগত কর্তব্যের শ্রেণী বিভাগ আছে। এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ফারাইয যা ঈমানের মৌলিক অঙ্গ, যেমন শাহাদাহ অথাৎ সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মা’বুদ নেই এবং হযরত মুহাম্মদ মোন্তোফা (সা) তাঁর রাসূল এবং কর্মে প্রতিফলন হচ্ছে সালাত, যাকাত, সিয়াম ও হজ্জের মাধ্যমে। আরো কম গুরুত্বপূর্ণ ফারাইয আছে, কিন্তু এগুলোও বাধ্যতামূলক। ফরযে কিফায়ার চেয়ে ফরযে আইনের গুরুত্ব অধিক। পিতার প্রতি সদাচার ফরযে আইন যা জিহাদের চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ, জিহাদ ফরযে কিফায়াহ। পিতার অনুমতি ছাড়া পুত্র জিহাদে অংশ নিতে পারবে না। এ সম্পর্কে প্রামাণিক হাদীস আছে। আবার ব্যাক্তিগত অধিকারের সাথে সংশ্লিষ্ট ফরযে আইনের ওপর সামাজিক অধিকারের সাথে সম্পৃক্ত ফরযে কিফায়াহ অগ্রাধিকার পাবে। মুসলিম ভূখন্ড আক্রান্ত হলে জিহাদ ফরযে আইন। তখন পিতার অধিকার গৌণ হয়ে যায়। এমনিভাবে ওয়াজিবের ওপর ফরয, সুন্নাতের ওপর ওয়াজিব ও মুস্তাহাবের ওপর সুন্নাতের অগ্রাধিকার রয়েছে। একইভাবে ইসলাম ব্যাক্তিগত আত্মীয়তার ওপর সামাজিক দায়িত্ব এবং এক ব্যাক্তির জন্যে উপকারী কাজের ওপর একাধিক ব্যক্তির উপকার হতে পারে এমন কাজে অগ্রাধিকার দেয়। নফল এবাদত, দান খয়রাতের চেয়ে দু’পক্ষের মধ্যেকার বিরোধ মীমাংসার প্রতিও ইবাদত ইসলাম অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে। একজন শাসককে তার নফল ইবাদতের চেয়ে তার সুবিচারের জন্যে বেশি পুরস্কার দেয়া হবে। অবক্ষয়ের যুগে মুসলমানরা যেসব ভুল করেছিলো সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিচে দেয়া হলো:
১. তারা উম্মার স্বাসংশ্লিষ্ট বৈজ্হানিক শিল্প ও সামরিক ক্ষেত্রে উদ্ভাবন ও উৎকর্ষ অর্জনের প্রচেষ্ঠা উপেক্ষা করেছে। এছাড়া ইজতিহাদ, আহকাম ও দাওয়া এবং স্বৈরশাসনের বিরোধিতা উপেক্ষা করেছে।
২. তারা ভাল কাজের আদেশ ও খারাপ কাজের নিষেধের মতো ব্যাক্তিগত কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করেনি।
৩.তারা কোনো মৌল বিশ্বাসকে কম গুরুত্ব দিয়ে অপর একটিকে বেশি পালন করেছে। তারা রমযানের নামাযের চেয়ে অগ্রাধিকার দিয়েছে। অজন্যে নামাযীর চেয়ে রোযাদারের সংখ্যা বেশি দেখা গেছে, বিশেষ করে মহিলাদের ক্ষেত্রে। এদের মধ্যে আবার কেউ কখনো সিজদাই করেনি। অনেকে যাকাতের চেয়েসালাতের বেশি গুরুত্ব দিয়েছে যদিও আল্লাহ তায়ালা কুরআনে একত্রে বাইশ বার এ দু’টো কাজের আদেশ দিয়েছেন। এজন্যে সাহাবায়ে কিরাম বলতেন, “যাকাত ছাড়া সালাত বাতিল।” আর হযরত আবু বকর (রা) তো যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন।
৪. পরযসমূহ ও ওয়াজিবাতের চেয়ে নাওয়াফিলের প্রতি বেশি গুরুত্ব দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে সূফীদের দৃষ্টান্ত উল্লেখযোগ্য। তারা নানা আচার-অনুষ্ঠান, যিকর ও তাসবীহর ওপর মনোযোগ দিয়েছেন; সামাজিক ও রাজনৈতিক অনাচার প্রতিরোধের মতো সামাজিক দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসেননি।
৫. তারা জিহাদ,ফিকাহ, আপোস-মীমাংসা, সৎকর্মে সহযোগিতা ইত্যাদির মতো সামাজিক দায়িত্ব অগ্রাহ করে ব্যাক্তিগত ইবাদত-বন্দেগীতে ব্যস্ত থেকেছেন।
৬. শেষত, অধিকাংশ মানুষ ঈমান, তাওহীদ, নৈতিক উৎকর্ষের মাধ্যমে আল্লাহর রেজামন্দি হাসিল ইত্যাদি মৌলিক বিষয় বাদ দিয়ে গৌণ বিষয়ে ওপর অযথা গুরুত্ব দিয়েছেন।
নিষিদ্ধ বিষয়গুলোরও শ্রেণীভেদআছে: যেমন, মাকরূহাত (ঘৃণা) কিন্তু গুনাহ নেই। যেগুলো ঘৃণা কিন্তু স্পষ্টবাবে নিষিদ্ধ নয়, এসব হালালের চেয়ে হারামের কাছাকাছি। মুতাশবিহাত (অস্পষ্ট বা নিগূঢ়) সেগুলোই যা অল্প লোকের কাছে জ্ঞাত এবং অজ্ঞতাবশত করে ফেলা হয়। এগুলো হারাম। সুস্পষ্ট নিষিদ্ধ বিষয়গুলো কুরআন ও সুন্নায় বিস্তারিত বণূনা করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন, “তোমরা কেন খাও না (গোশত) যাতে আল্লাহর নাম উচ্চারিত হয়েছে যখন তিনি নিষিদ্ধ বিষয়গুলো বিস্তারিত ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন?” (৬:১১৯)
এই নিষেধাজ্হা দু’ভাগে বিভক্ত: ছোট ও বড়। ছোট বিষয়গুলো অপসৃত হয় সালাত, সিয়াম ও দান-খয়রাতের মাধ্যমে। কুরআনুল করীম থেকে আমরা জানি, “সুকৃতি দুষ্কৃতিকে অপরিসারিত করে।” (১১:১১৪)
রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সুন্নাত থেকে আমরা জানি, নিয়মিত সালাত ও সিয়াম আদায় করলে এরন মাঝখানের ছোট
ছোট গুনাহ মাফ হয়ে যায়। অবশ্য বড় পাপ কেবল খালেস তওবার মাধ্যমে মাফ হতে পারে। এর মধ্যে সবচেয়ে কবীরা গুনাহ হচ্ছে শিরক-আল্লাহর সাথে অন্য সত্তাকে শরীক করা। এ গুনাহর কখনো মাফ নেই। আল্লাহ বলেন: “আল্লাহ্ তাঁর সাথে শরীক করার অপরাধ মাফ করেন না, এছাড়া অনান্য অপরাধ যাকে ইচ্ছে মাফ করে দেন, যে কেউ আল্লাহ্র সাথে শরীক করে সে এক মহাপাপ করে।” (৪:৪৮)
অতঃপর হাদীসে উল্লেখিত পাপগুলো হচ্ছে: পিতামাতার অবাধ্যতা, মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া, যাদু, খুন, সুদ, এতীমের সম্পদ আত্মসাৎ এবং মিথ্যা সাক্ষ্য করে সতী মুসলিম মহিলাদের বিরুদ্ধে যিনার অপবাদ।
নিম্মোক্ত বিষয়গুলো থেকে ত্রুটি ও বিভ্রান্তি দেখা দেয়:
ক. মানুষের মধ্যে মুহাররামাতের চেয়ে মাকরূহাত ও মুতাশাবিহাতের প্রতি বাধা দেয়ার প্রবণতা বেশি দেখা যায়। অন্যদিকে ওয়াজিবাতকে উপেক্ষা করা হয়। সুস্পষ্ট হারামের পরিবর্তে মতভেদের বিষয়গুলো নিয়ে বেশি ব্যগ্রতা।
খ. অনেক লোক ভাগ্য গণনা, যাদু, মাযারকে নামাযের স্থান হিসেবে ব্যবহার, মৃতদের উদ্দেশ্য পশু উৎসর্গ, মৃতদের কাছ থেকে সাহায্য প্রার্থনা ইত্যাদি কবীরা গুনাহর পরিবর্তে ছগীরা গুনাহ প্রতিরোধে বেশি ব্যস্ত। অথচ কবীরা গুনাহগুলো তাওহীদী চেতনাকে দূষিত করে।
একইভাবে বিভিন্ন মুসলমানের আচরণও বিভিন্ন। কোনো কোনো ধার্মিক যুবক জ্ঞান, ঈমান ও শক্তির ব্যাপারে অন্য সকলকে এমন চোখে দেখে যেন তারা সবাই সমান। সুতরাং তারা সাধারণ ও জ্ঞানী-গুণী মানুষের মধ্যেও পার্থক্য করতে পারে না। এছাড়া পুরানো মুসলমান ও ন্ওমুসলিম এবং প্রাকৃতিক ভিন্নতার দিকে লক্ষ্য রেখেই শ্রমসাধ্য ও সহজবোধ্য, ফারাইয ও নাওয়াফিল, বাধ্যতামূলক ও ঐচ্ছিক অধিকারী করলাম আমার বান্দদের মধ্যে তাদেরকে যাদেরবে আমি মনোনীত করেছি; তবে তাদের মধ্যে কেউ নিজের ওপর যুলুম করে, কেউ মধ্যপন্থী এবং কেউ আল্লাহর ইচ্ছায় কল্যাণকর কাজে অগ্রগামী। এটাই মহাঅনুগ্রহ।” (৩৫: ৩২)
এ প্রসঙ্গে ‘যে ব্যাক্তি ভুল করেছে’ বলতে ‘যে নিষিদ্ধ কাজ এড়িয়ে গেছে এবং ‘যার ফরয কর্তব্য পালন অসম্পূর্ণ’ বোঝানো হয়েছে। ‘যে ব্যক্তি মধ্যমপন্থা অনুসরণ করে’ বলতে ‘যে কেবল অবশ্য পালনীয় কাজ সম্পন্ন করে এবং নিষেধাজ্ঞা পরিহার করে’ এমন ব্যক্তিকে বোঝানো হয়েছে। যে ব্যক্তি সৎকর্মে অত্যন্ত অগ্রণী বলতে ‘যে ব্যক্তি বাধ্যতামূলক ্ও অনুমোদিত কর্তব্য পালন করে এবং নিষিদ্ধ কাজ’ কেবল পরিহার করে না সকল ধরনের বাজে ও নিন্দনীয় কাজ থেকে বিনত থাকে এমন ব্যক্তিকে বোঝানো হয়েছে। উপরিউক্ত ধরনের সকল লোকই ইসলামী উম্মাহর অর্ন্তভুক্ত যাদেরকে আল্লাহ্ কিতাব দিয়েছেন। এই দৃষ্টিতে কেউ ভুল করলেই তাকে ফিসকের অভিযোগে অভিযুক্ত করা ঠিক হবে না অথবা মতভেদ আছে এমন আমল দেখলেই তাকে হারাম ফতোয়া দেয়াও যুক্তিযুক্ত নয়। যেসব তরুণ মুসলমান এরূপ তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে তাদের এ কথা ভুললে চলবে না যে, কুরআন স্পষ্টভাবে ছোট ও বড় গুনাহর পার্থক্য রেখা টেনে দিয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন:
“আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা আল্লাহর। যারা খারাপ কাজ করে তাদেকে তিনি দেন মন্দ ফল আর যারা ভাল কাজ করে তাদেরকে দেন উত্তমপুরস্কার, তারাই বিরত থাকে গুরুতর পাপ ও অশ্লীল কাজ থেকে, ছোটখাট অপরাধ করলেও। তোমার প্রতিপালকের ক্ষমা অপরিসীম।” (৫৩:৩১-৩২)
ছোটখাট ত্রুটির প্রতি সহনীয় দৃষ্টভঙ্গির ব্যাখ্যা একটি আরবী শব্দ ‘লামাম’-এ (ছোট ত্রুটি) পাওয়া যায়। লামামের দু’টি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্যা আছে।্আল-হাফিজ ইবনে কাছির (র) সূরা আন-নিসার ২৫৫-২৫৬ নং আয়াতের ব্যাখ্যা দিতে বলেছেন: ‘আলমুহসিমুনন’ শব্দের ব্যাখ্যা হচ্ছে যারা কবীরা গুনাহ ও লজ্জাকর কাজ পরিহার করে অথাৎ বড় বড় নিষিদ্ধ কাজ পরিত্যাগ করে। এরূপ লোক যদি ছোটখাট ভুল করে বসে, আল্লাহ্ তাকে মাফ করবেন এবং রক্ষা করবেন; যেমন তিনি আরেকটি আয়াতে ওয়াদা করেছেন:
“তোমাদেরকে যা নিষেধ করা হয়েছে তার মধ্রে যা গুরুতর তা হতে বিরত খাকলে তোমাদের লঘু পাপগুলো মোচন করব এবং তোমাদেরকে সম্মানজনক স্থানে দাখিল করব।” (৪:৩১)
তিনি আরো বলেন, “...যারা কবীরা গুনাহ ও লজ্জাকর কাজ পরিহার করে, কেবল ছোটখাট ভুল (করে)” এখানে ছোটখাট ত্রুটিকে (লামাম) সম্পূর্ণ বাদ দেয়া হয়েছে, কেননা এগুলো ছগীরা গুনাহ ও লজ্জাকর কাজের উপ-শ্রেণীভুক্ত।
ইবনে কাছির (র)-এর পরে বলেছেন: ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আবু হুরায়রাহ (রা) থেকে নিম্মোক্ত হাদীস শোনার পরেই কেবল লামেমের (ছোট খাট ত্রুটি) বিষয়টি আমি উপলব্ধি করেছি: ‘আল্লাহ্ পাক আদমের পুত্রের (মানুষ) জন্যে ব্যভিচারের অংশ নির্দিষ্ট করে রেখেছেন যা সে অনিবার্যভাবেই করবে। চোখের যিনা হচ্ছে একদৃষ্টে সেই বস্তু দেখা যা নিষিদ্ধ করা হয়েছে; জিহবার যিনা হচ্ছে উচ্চারণ; অন্তরে কামনা-বাসনার উদ্ভব এবং গোপন অংগের মাধ্যমে যার আস্বাদন অথবা প্রত্যাখ্যান।”
তাই আবু মাসউদ (রা) ও আবু হুরায়রাহ (রা) বলেন, “লামামমের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে: ‘স্থির দৃষ্টিতে তাকানো, চোখের ইশারা, চুম্বন এবং প্রকৃতপক্ষে ব্যভিচার করা ছাড়াই যৌন সঙ্গমের নিকটবতর্তী হওয়া।”
লামামের অন্য ব্যাখ্যাও ইবনে আব্বাস (রা) দিয়েছেন: লজ্জাকর কাজ বটে কিন্তু এর জন্যে অনুতপ্ত হয়। তিনি পদ্যাকারে একটি হাদীসের উদ্ধৃত দেন যার রূপান্তর করলে দাঁড়ায়, “হে আল্লাহ, আপনার ক্ষমা সীমাহীন, কেননা আপনার বান্দাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে ছোটখাট ভুল করে না।” (ইবনে কাছির)
আবু হুরায়রাহ (রা) ও আল হাসান (রা) যুক্তি দেখান: গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা না করেই যে ভুল করা হয় তাই লামাম এবং যা ঘন ঘন করা হয় না। উপরিউক্ত আলোচনার তাৎপর্য দাঁড়ায়: যারা নিয়মিত কবীরা গুনাহ করে না তাদের জন্যে ইসলামের অঙ্গন বিস্তৃত; কেননা যারা অনুতপ্ত তাদের জন্যে আল্লাহর দয়া প্রশস্ত।
যারা নিয়মিত ফরয কাজ আদায় করে, তাদের নগণ্য ভুলগুলোকে উপেক্ষা করা যায় কিভাবে, তার একটি শিক্ষণীয় দৃষ্টন্ত উমর ইবনে খাত্তাব (রা)-এর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পাওয়া যায়। বর্ণিত হয়েছে, আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) যখন মিসরে ছিলেন তখন তার কাছে কিছু লোক গিয়ে বললো, অনেকেই আলকুরআনের শিক্ষা মেনে চলছে না এবং তারা এ ব্যাপারে খলীফা উমর (রা) তখন তাদেরকে মদীনায় উমর (রা)-এর কাছে নিয়ে গেলেন এবং সফরের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করলেন। উমর (রা) তখন ঐ লোকেদের সাথে একটি বৈঠকের ব্যবস্থা করতে বললেন। বৈঠকে তার নিকটতম লোকটিকে উমর (রা) ব/ররেন, “সত্যি করে বলো, তুমি কি গোটা কুরআন পড়েছে?” লোকটি ইতিবাচক জবাব দিল। তারপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, “তুমি নিজে কি এর শিক্ষা কড়াকড়িভাবে মেনে চলো যেন তোমার হৃদয় ও কাজকর্ম পরিশুদ্ধ হয়?” লোকটি প্রতিটির জবাবে নেতিবাচক জবাব দিলো। উমর (রা) তখন বললেন, “তুমি কি (নিষিদ্ধ বিষয় ও বস্তুর) দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকানোর ব্যাপারে, মুখে উচ্চারণ ও বস্তুর জীবনের আচরণে এ রশিক্ষাগুলো কড়াকড়িভাবে মেনে চলেছ?” লোকটি প্রতিটির জবাবে নেতিবাচক জবাব দিলো। উমর (রা) তখন গ্রুপের প্রত্যেকলোককে এই প্রশ্ন করলে প্রত্যেকে নেতিবাচক জবাব দিল।
এরপর উমর (রা) বললেন, “তাহলে তোমরা কি করে খলীফার কাছে দাবী করতে পার যে, তোমরা যেভাবে আল্লাহর কিতাবকে বুঝেছ তাই মানুষকে মানতে বাধ্য করি যা তোমরা নিজেরাই করতে ব্যর্থ হয়েছ বলে স্বীকার করলে? আমাদের প্রভু জানেন যে, আমরা প্রত্যেকে কিছু না কিছু খারাপ কাজ করে ফেলি।” অতঃপর তিনি কুরআনের এই আয়াতটি পাঠ করলেন, “তোমরা যদি জঘন্যতম কাজগুলো থেকে বিরত থাকো তাহলে আমি তোমাদের সকল খারাপ কাজকে বিদূরিত করবো এবং মহান মর্যাদার তোরণে তোমাদের প্রবেশ করাবো।” (৪:৩১)
লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে উমর (রা) বললেন, “মদীনার বাসিন্দারা কি জানে তোমরা কি জন্যে একানে এসেছ?” তারা নেতিবাচক জবাব দিলে তিনি বললেন, “তারা যদি জানত তাহলে তোমাদেরকে আমি (শাস্তি দিয়ে) দৃষ্টান্ত বানাতাম।” (ইবনে কাছীর)
কুরআনুল করীমের গভীর জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে উমর (রা) তাৎক্ষণিকভাবে সরেজমিনে বিষয়টির নিষ্পত্তি করে দিলেন এবং এভাবে অহঙ্কারও গোঁড়ামির গোড়া কেটে দিলেন। এ ব্যাপারে তিনি যদি এতোটুকু দুর্বলতা দেখাতেন তাহলে সুদূরপ্রসারী মারাত্মক ফিতনা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠার আশঙ্কা ছিলো।
৩. অন্যের প্রতি সহৃদয় অনুভূতি
ব্যক্তিগতভাবে মানুষের ক্ষমতার তারতম্য এবং জীবনের রূঢ় বাস্তবতার বিভিন্ন স্তর থাকে। অন্তর্দৃষ্টি ও ফিকহের জ্ঞানের পাশাপাশি অন্যের এই বাস্তবতার প্রতিও পরস্পরের সহৃদয় অনুভূতি থাকা আবশ্যক। আন্দোলনের ক্ষেত্রে সকলের কাছ থেক হযরত হামযাহ ইবনে আবদুল মুত্তালিবের (রা) মতো শাহাদাতের শৌর্য প্রত্যাশা করা ঠিক হবে না। এটি এমন মহৎ গুণ, গভীরতম নিষ্ঠা ও অধ্যাবসায় ছাড়া যার প্রকৃত মর্ম খুব কম লোকই অনুধাবন করতে পারে।
কেউ কেউ শান্তভাবে সত্যের পক্ষে কথা বলে তৃপ্তিবোধ করে; অন্যেরা তাদের ধারনণা অনুযায়ী বিরাজমান মারাত্মক অবস্থার প্রেক্ষিতে নীরব থাকই নিরাপদ মনে করে। আবার অনেকে মনে করেন আগা নয়, গোড়া থেক সংস্কার কাজ চালাতে হবে। এজন্যে তারা ব্যাক্তি বিশেষের প্রতি তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। তারা মনে করে, এসব লোকের দৃষ্টিভঙ্গি সংস্কৃত ও পরিশুদ্ধ করতে পারলে কাঙ্খিত পরিবর্তন আসতে পারে। কিন্তু এটা বলাবাহুল্য, পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী ধর্মনিরপেক্ষ ব্যবস্থা নির্মূল করতে হলে সুনির্দিষ্ট ও দীর্ঘমেয়াদী কর্মসূচীর ভিত্তিতে একটি ইসলামী সঙগঠনের নেতৃত্বে সম্মলিত সংগ্রাম ছাড়া গত্যন্তর নেই। অবশ্য শরীয়ত এক মুন্কার থেকে যেন আরেকটি বড় মুনকারের সৃষ্টি না হয় সেজন্যে অনেক ক্ষেত্রে নীরবতাকে যুক্তিযুক্ত মনে করে। এ প্রসঙ্গে কুরআনুল করীমে হযরত মূসার (আ)-এর ঘটনা থেকে শিক্ষা পাওয়া যায়। মূসা (আ:) -কে তার স্থলাভিষুক্ত করে যান। কিন্তু তিনি চলে যাওয়ার পরপরই ইসরাঈলীরা সামেরিদের পরামর্শে একটি সোনার গো-মূর্তি বানিয়ে পূজো করতে শুরু করে। এই বিচ্যুতির বিরুদ্ধে হারুন (আ)-এর বক্তব্য শুনতেও তারা অস্বীকার করে। কুর্আন বলছে:
“হারুন তাদেরকে আগেই বলেছিলেন, হে আমার স্বজাতি! তোমাদেরকে এর দ্বারা পরীক্ষায় ফেলা হয়েছে। তোমাদের দয়াময়; সুতরাং তোমরা আমাকে অনুসরণ কর এবং আমার আদেশ মেনে চল। তারা বলেছিলো: আমাদের কাছে মূসা ফিরে না আসা পর্যন্ত আমরা পূজা হতে কিছুতেই বিরত হব না।” (২০:৯০-৯১)
তাদের অনমনীয়তা দেখে হারুন (আ) নিশ্চুপ হয়ে গেলেন। মূসা (আ) ফিরে এসে ক্রোধে ও দুঃখে অগ্নিশর্মা হয়ে হারুন (আ)-কে রূঢ়ভাবে তিরস্কার করলেন। কুরআনের বর্ণনা, “মুসা বলল, ও হারুন! তুমি যখন দেখলে তারা পথভ্রষ্ট হয়েছ তখন কিসে তোমাকে নিবৃত্ত করল- আমার অনুসরণ করা হতে? তবে কি তুমি আমার আদেশ অমান্য করলে!” (২০:৯২-৯৩)
হারুন (আ) জবাব দিলেন : “হে আমার সাহোদর! আমার দাড়ি ও চুল ধরে টেনে না; আমি আশংকা করেছিলাম যে, তুমি বলবে, তুমি বনী ইসরাঈলেদের মধ্যে বিভদ সৃষ্টি করেছে এবং তুমি বলবে, তুমি আমার কথা পালনে যত্নবান হওনি।” (২০ : ৯৪) সুতরাং দেখা যাচ্ছে সামাজি ঐক্য ও সম্প্রীতির স্বার্থে হারুন (আ) হযরত মূসা (আ) ফিরে না আসা পর্যন্ত নীরবতা অবলম্বন করেছেন। এই ঘটনার সাথে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাদীসের সাজুয্য লক্ষ্যণীয়। তিনি বলেছিলেন, তাঁর অনুসারীরা সবেমাত্র পৌত্তলিকতা ত্যাগ করে কা’বা নির্মাণ থেকে বিরত থেকেছেন।
রাসূলুল্লাহ (সা)-এর অনান্য আদেশ থেকেও এরূপ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়্। যেমন যদি অত্যাচারী-অনাচারী শাসককে হটিহটিয়ে সৎ ব্যাক্তির সরকার কায়েমের ক্ষমতা না থাকে তাহলে শাসকের অবিচার সহ্য করার কথা আছে। কেননা প্রতিবাদ করতে গিয়ে যেন বৃহ্ত্তর ফিতনার সৃষ্টি না হয়, মুসলমানদের অযথা রক্তপাত বা সামাজিক স্থিতিশীরতা যেন বিনষ্ট না হয় অথাৎ বাস্তব ফল ছাড়া কেবল অরাজকতা সৃষ্টি হতে পারে এমন প্রতিবাদের চেয়ে নীরবতাই কাম্য। অন্যথায় পরিস্থিতি এমনও হতে পারে যে, কুফরী অথবা রিদ্দাহর দিকেও মোড় নিতে পারে। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, “যতোক্ষণ না তুমি প্রকাশ্য কুফরী প্রত্যক্ষ কর যার পক্ষে তোমার কাছে আল্লাহ্র তরফ থেকে প্রমাণ আছে।” ((বুখারী, মুসলিম)
দু’টি দৃষ্টান্ত অনিশ্চিত সাফল্যের মুখে ঐক্য বজায় রাখার ওপর আলোকপাত করেছে। পক্ষান্তরে ইসলামী শিক্ষা পালনে ক্ষেত্রে যেসব ভাববাদী মুসলমান চরম পূর্ণতা দেখতে চায় অযথা যারা একেবারে বর্জন করতে চায় তাদের উভয়ের জন্যে এই ঘটনাগুলো শিক্ষণীয়। এদের কাছে কোনো মধ্যপন্থা নেই। ভাববাদীরা মুন্কার উচ্ছেদ শক্তি প্রয়োগকেই শেষ হাতিয়ার মনে করেন। তারা অন্য দু’টি পথ অর্থাৎ কথা ও হৃদয় দিয়ে প্রতিরোধের কথা বেমালুম ভুলে যান। মোটকথা, প্রতিটি উপায় প্রয়োগ নির্ভর করে ব্যাক্তির ক্ষমতা ও পরিস্থিতির ওপর। আশ-শরীয়াহ বিভিন্ন পরিস্থিতি ও প্রয়োজনের কথা বিবেচনা করার ওপর এতো দূর গুরুত্ব দিয়েছে যে, নিরূপায় অবস্থায় হারামও হালাল হয়ে যায় এবং ওয়াজিব স্থগিত হয়। ইমাম ইবনে তাইমিয়া (র) এবিষয়ে বুদ্ধিসীপ্ত আলোচনা করেছেন। তিনি লিখেছেন:
“আল্লাহ্ তা#য়ালা কুরআনুল করীমে বিভিন্ন জায়গায় বলেছেন যে, তিনি ক্ষমতার বাইয়ে অতিরিক্ত বোঝা মানুষের ওপর চাপাতে চান না।” তিনি বলেন, “আল্লাহ্ কারো ওপর এমন কোন কষ্টদায়ক দায়িত্ব অর্পণ করেন না যা তার সাধ্যাতীত।” (২:২৮৬) “আমরা কাউকেই তার সাধ্যাতীত অর্পণ করি না।” (৭:৪২)
“কাউকেই তার সাধ্যতীত কার্যভার দেয়া হয় না এবং আল্লাহ যাকে যে সামর্থ দিয়েছেন তদপেক্ষা গুরুতর বোঝা তিনি তার ওপর চাপন না।” (৬৪:১৬) ঈমানদারই তাঁর কাছে প্রার্থনা করেছে: “হে প্রভু, আমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর যেমন গুরুদায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন আমাদের ওপর তেমন দায়িত্ব অর্পণ করবেন না। হে প্রভু! এমন ভার আমাদের ওপর অর্পণ করবেন না যা বহন করার শক্তি ্আমাদের নেই।” (২:২৮৬)
আল্লাহ্ তাদের প্রার্থনা কবুল করেছেন। এসব আয়াত প্রমাণ করেছে যে, তিনি মানুষের ওপর এমন বোঝা চাপান না যা সে বহন করতে পারবে না। এটা নিশ্চিত যে, জাহমিয়া, কাদিরিয়া ও মুতাযিলা দর্শনের সাথে এর কোনো সংগতি নেই। এখানে একটি বিষয় পরিষ্কার বুঝে নিতে হবে যে, যদি কোনো শাসক, ইমাম, বুদ্ধিজীবি, ফকীহ অথবা মুফতী আল্লাহ্র খালেস ভয়ে তার সাধ্য অনুযায়ী যে ইজতিহাদ করবে তাহলে বুঝতে হবে আল্লাহ তার কাছ থেকে এটাই চেয়েছিলেন। তার সিদ্ধান্ত ভুল হোক, শুদ্ধ হোক, তাকে শাস্তি দেয়া হবে না। এর বিপরীত কাদিয়রা ও মুতাযিলারা যে ধারণা পোষণ করে তা বাতিল।
কাফিরদের বেলায়ও একই বিষয় প্রযোজ্য। যারা কুফরীর দেশে রাসূলের দাওয়াত পেয়ে তাঁকে রাসূল বলে স্বীকার করলেন এবং তাঁর ওপর অবতীর্ণ ওহীকে বিশ্বাস করে যথাসাধ্য আনুগত্য করলেন-যেমন নাজ্জাশী ও অন্যান্য, কিন্তু ইসলামের ভূখন্ডে যেতে না পরার দরুন শরীয়তকে সামগ্রিকভাবে মানতে পারলেন না; কারণ তাদেরকে দেশত্যাগের অনুতি দেয়া হয়নি অথবা প্রকাশ্যে আমলের সুযোগ পাননি এবং তাদেরকে সমগ্র শরীযাহ শিক্ষা দেয়ার মতো লোক ছিল না। এমন সকল মানুষের জন্যে আল্লাহ জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এরূপ আরো উদাহরণ আছে। আল্লাহ তায়ালা ফেরাউনের লোকদের মধ্যে যারা বিশ্বাসী ছিলো তাদের সম্পর্কে বলছেন: “এবং তোমাদের কাছে পূর্বে ইউসুফ এসেছিলেন স্পষ্ট নিদের্শন সহকারে, কিন্তু তিনি যা নিয়ে এসেছিলেন তাতে তোমরা বার বার সন্দেহ পোষন করতে। অবশেষে তিনি যখন ইন্তিকাল করলেন তখন তোমরা বলেছিলে, তারপরে আল্লাহ্ আর কাউকে রাসূল করে পাঠিবেন না।” (৪০-৩৪)
নাজ্জাশী খৃস্টানদের রাজা ছিলেন; কিন্তু তিনি তাদেরকে ইসলাম গ্রহণ করতে বললে তারা অস্বীকার করলো। কেবল মুষ্টিমেয় লোক তাকে অনুসরণ করেছিলো। তিনি যখন মারা গেলেন তখন তার জানাযা পড়ারও কেউ ছিলো না। রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনায় তার জানাযা পড়েন এবং উপস্থিত সকলকে বলেন, “আবিসিনিয়ায় তোমাদের মধ্যেকার একজন সৎ কমর্মশীল ভাই মারা গেছেন।” (বুখারী ও মুসলিম)
যদিও নাজ্জাশী ইসলামের অনেক শিক্ষা মানতে পারেননি, দেশত্যাগ করেননি, জিহাদে অংশ নেননি অথবা হজ্জ্ও করেননি। এটাও বর্ণিত আছে যে, তিনি পাঁচ ওয়াক্ত নামায, সিয়াম অথবা যাকাতের কতর্তব্য পালন করতে পারেননি; কেননা তার ঈমানের কথা প্রকাশ হয়ে পড়লে জনগণ তার বিরুদ্ধে চলে যেতে পারে। আমরা জানি, তিনি আল-কুরআনের বিধানও প্রয়োগকরেননি, যদিও আল্লাহ পাক তাঁর রাসূলকে আহলে কিতাবরা চাইলে তাঁর বিধান অনুযায়ী ফায়সালা করার আদেশ দিয়েছিলেন। আবার আল্লাহ্ তাঁর রাসূলকে এই মর্মে সতর্কও করে দিয়েছেন, “আহলে কিতাবরা যেন তাকে ওহীর অংশ বিশেষ খথেকেও বিচ্যুত করার জন্যে প্রলুব্ধ করতে না পারে।” কঠোর ন্যায়পরায়ণতার জন্যে উমর ইবনে আবদুল আজীজ (রা)-কে অনেক বিড়াম্বনা সইতে হয়েছে। এজন্যে তাকে বিষ প্রয়োগও করা হয়েছিলো বলে জানা যায়। কিন্তু নাজ্জাশী এবং তার মতো অন্যরা এখন জান্নাতে শান্তিতে আছেন যদিও তারা শরীয়তকে পূর্ণরূপে পালন ও প্রয়োগ করার সুযোগ পাননি, বরং তাই করেছেন যা তাদের কাছে প্রযোজ্য মনে হয়েছে। (মাজমুয়া আল ফাতওয়া)
৪. আল্লাহর সৃষ্টি রীতির জ্ঞান
ইসলাম যুক্তি ও অনুসন্ধিৎসার ধর্ম। এ কারণে পর্যায়ক্রম, সহিষ্ণুতা ও ক্রমিক পূণর্ণতার তাৎপর্য সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করা ইসলামের অন্যতম লক্ষ্য। মানূষ, বিশেষ করে তরুণদের মধ্যে দ্রুতির প্রবণতা অন্তর্নিহিত। অবশ্য এটি আমাদের যুগেরও বৈশষ্ট্য। এজন্যে আজ ফসল বুনে কালই তা কাটতে চায়। কিন্তু আল্লাহ্র সৃষ্টিরীতি অনুযায়ী এরূপ দ্রুতির কোনো অবকাশ নেই। গাছ থেকে ফল আহরণ করতে হলে এর পর্যায়ক্রমে অতিক্রম করতে দিতে হবে। মানুষের সৃষ্টি ত এর প্রকৃষ।ট নজীর। কুরআন বলছে:
“অতঃপর আমি শুক্রকে পরিণত করি রক্তপিণ্ড, তারপর রক্তপিণ্ডকে পরিণত করি মাংসপিণ্ডে, তারপর মাংসপিণ্ডকে পরিণত করি অস্থিপঞ্জরে, পরে অস্থিপঞ্জরকে মাংসে আবৃত করে দিই; অবশেষে তাকে গড়ে তুলি অন্য এক সৃষ্টিরূপে। অতএব সর্বোত্তম স্রষ্টা আল্লাহ্ কত মহান!” (২৩-১৪)
এমনিভাবে মানুষও শিশু থেকে পর্যায়ক্রমে প্রাপ্তবয়স্ক পরিণত হয়। একইভাবে আল্লাহ্র সুনান অনুযায়ী মানুষের জীবনেও বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে। অনুরূপভাবে আল্লাহ্র দ্বীন বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে অবশেষে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছে। তখন এই আয়াত নাযিল হয়েছে:
“আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পূর্ণাঙ্গ করলাম, তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম, এই ইসলামকেই তোমাদের দ্বীন মনোনীত করলাম।” (৫:৩) বিষয়টি অন্তত্য সহজ সরল; কিন্তু চারদিকের অবস্থা দেখে উৎসাহী তরুণরা এতোই বিক্ষুব্ধ যে, এই জ্ঞান তাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। তারা রাতারাতি ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করে সব সমস্যার সমাধানকরে ফোলতে চায়। তারা তাদের সম্মুখবর্তী বাধা-বিপত্তিকে লঘু দৃষ্টিতে দেখতে চায়। বস্তুত তাদের এই উভয় সংকটকে একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝানো যায়। এক ব্যক্তি আবু শিরিন (র) - কে একটি স্বপ্নের তাবির বলার অনুরোধ করেছিলো। সে স্বপ্ন দেখেছিলো যে, সে শুকনো জমিতে সাঁতার দিচ্ছে, ডানা ছাড়াই উড়ছে।” ইবনে শিরিন (র) তাকে বললেন, তিনিও এমন অনেক স্বপ্ন ও আকাংখা পোষণ করেন। হযরত আলী (রা) তার পুত্রকে হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলেন, “...ইচ্ছার ওপর নির্ভর করা থেকে সাবধান, এগুলো হচ্ছে আহাম্মকের উপকরণ।” অতএব এটা স্বতঃসিদ্ধ যে, বিপরীত বাস্তবতাকে কেবল ইচ্ছার হাতায়ার দিয়ে পাল্টানো যাবে না। প্রসঙ্গত একিট অমূল্য বইয়ের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি: ‘হাত্তা ইয়ুগাইয়িরু মা বিআনফুসিহিম’ (যতোক্ষণ না তারা নিজেরা পরিবর্তিত হয়)। এটি লিখেছেন সিরীয় মনীষী জাওদাত সাঈদ (র) বইটিতে আত্মা ও সমাজের পরিবর্তন ধারা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আলোচনার ভিত্তি হচ্ছে কুরআনের এই আয়াত : “নিশ্চয়ই আল্লাহ্ কোনো জাতার অবস্থা পরিবর্তন করেন না যতোক্ষণ না তারা নিজেদের অবস্থা নিজেরা পরিবর্তন করে।” (১৩ : ১১)
এবং ‘কারণ, আল্লাহ্ কোন সম্প্রদায়কে প্রদত্ত সৌভাগ্য পরিবর্তন করেন না যতোক্ষণ না তারা নিজেরাই পরিবর্তিত করে দেয় নিজের জন্য নির্ধারিত বিষয়।” (৮ : ৫৩)
বইটির ভূমিকার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ হচ্ছে : “মুসলিম তরুণদের মধ্যে অনেকেরই ইসলামের জন্য জান ও মাল কুরবানীর দৃঢ় প্রত্যয় রয়েছে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে এদের মধ্যে মাত্র মুষ্টিমেয় সংখ্যক তরুন জ্ঞানের একটি বিশেষ শাখায় অথবা দুর্বোধ্য সত্যকে উন্মোচিত করার লক্ষ্যে অধ্যয়নে উৎকর্ষ অর্জনে আগ্রহ প্রকাশ করে থাকে। উদাহরণস্বরূপ ঈমান ও আমল তথা বর্ণনা ও বাস্তবের শ্রণীবিভাগ ইত্যাদি সমস্যা রয়েছে। এসব বিষয় এমন সমস্যা সৃষ্টি করে যার বস্তুনিষ্ঠ ও তথ্যপূর্ণ সমাধান না হলে গঠনমূলক সংস্কার অসম্ভব। ইসলামী বিশ্ব এখনো গবেষণা ও লেখনীর র্মম উদ্ধার করেত পারছে না। কারণ তারা এখনো মনে করে যে, ‘মসির চেয় অসি শক্তিশালী।’ এজন্যেই আমাদের শিক্ষা-দীক্ষা স্তবিরতায় পর্যবসিত হয়েছে। ‘ঝাঁপ দেয়ার আগে চিন্তা করার কথা আমরা ভুলেই গেচি। ফলত উপরিউক্ত জ্ঞানের ক্ষেত্রে সর্বাত্মক বিভ্রান্তি বিরাজ করছে। এসবের মধ্যেকার পারস্পরিক সমন্বয় ও শৃংখলার বিষয়টি আমারা অধ্যায়ন বা উপলব্ধির চেষ্টা করছি না।
তদুপরি মুসলিম বিশ্বে ঈমানের অবস্থা সম্পর্কেও আমরা এখানে সতক”র্ পর্যালেচনা করছি না। এটার অর্থ এই নয় যে, মুসলমানদের ইমান ও ইসলাম সম্পর্কে মৌলিক জ্ঞান নেই। আমরা বরং মানসিক অবস্থার কথা বলতে চাই যা অবশ্যই মনের গহীন থেকে পরিবর্তন করতে হবে। আর ঐ পরিবর্তনই কেবল সৃষ্টিতে সক্ষম।
আত্মত্যাগ ও সাদকার প্রকৃত মর্ম গভীরভাবে উপলব্ধি না করে এখনো বিশ্বাস করা হয় যে, ঐ দু’টো সবচেয়ে মহত্তম পুণ্য। সুপরিকল্পিত ও সুচিন্তিত কৌশলের অনুপস্থতিতে কেবল কুরবানী করলেই এর লক্ষ্য অর্জিত হতে পারে না। অবুঝ বিশ্বাস তরুণ মনে জানমাল কুরবানীর আবেগ সৃষ্টি করে বটে, এর তাৎপর্য অধ্যয়ন ও উপলব্ধির চেতনা সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয়। তাৎক্ষণিক ভাবাবেগ বা চাপ থেকে কুরবানীর প্ররণা আসে; কিন্তু জ্ঞানের অন্বেষার জন্যে দাকার অবিশ্রান্ত অধ্যবসায়, চৈতন্য, অন্তদৃষ্টি ও সমীক্ষার মানসিকতা। আর এটিই পরিশেষে নিশ্চত সাফল্যের সম্ভাবনা সমুজ্জ্বল করে।
অবশ্য কোনো কোনো তরুণ বিভিন্ন বিভাগে অধঘ্যয়ন-পঠনের কাজে মনোনিবেশ করলেও শেষাবধি একঘেঁয়ে ক্লান্তি অনুভব করে উৎসাহ হারিয়ে ফেলে এবং জ্ঞান-গবেষণা হিমাগারে আশ্রয় নেয়। আমাদেরকে গভীর পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে এই জড়তা ও স্থাবিরতার কারণ খুঁজে বের করতে হবে।
আত্মোপলব্ধি ও আত্মসচেতনতা ছাড়াই দ্রুত পরিবর্তন সাধনের প্রবণতা অবান্তর। বিদ্যমান বাস্তবতার প্রতিক্রিয়া উলব্ধি এক জিনিস, আমাদের নিজস্ব ভূমিকা সম্পর্কে সচেতনতা অন্য জিনিস। এ ব্যাপারটি গুরুত্বপূর্ণ বিধায় আল কুরআনের এই শিক্ষার ওপরেও আলোকপাত করা হয়েছে। কুরআনে সমস্যার অন্তস্থল হিসেবে খুদী বা অহমকে চিহ্নিত করা হয়েছে, বাইরের অসদাচরণ বা অনাচার নয়। কুরআনুল করীমে সম্পদের যে কাঠামো নির্ধারণ করা হয়েছে তার মূল কথা হলো এটাই। এই সহজ সরল সত্যটি উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হলে আমাদের দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়ে যায় এবং এই তখন নৈরাশ্য, বৈরাগ্য ও স্বৈরাচারী দর্শনের উদ্ভব ঘটে।
অতএব মারাত্মক স্বআরোপিত অবিচার হচ্ছে মানুষ, মহাজগত ও সমাজের অন্ত র্নিহিত অনুষঙ্গ অনুধাবনে ব্যর্থতা। ফলত কোন্ অবস্থানে নিজেকে স্থাপিত করলে মানুষ আল্লাহ্র সুনান (রীতি) অনুযায়ী মানবীয় ও প্রাকৃতিক সম্ভাবনাকে সর্বোত্তম উপায়ে আহরণ করতে সক্ষম, তার বিচার করতে ভুল করে সে ব্যর্থতার গ্লানি বহন করে। এই দৃষ্টিতে, সমস্যার সম্মুখীন হলে দু’টি মানসিকতার উদ্ভব হয়। প্রথমত, এটা বিশ্বাস করা যে, সমস্যাটি নির্দিষ্ট ধারায় নিয়ন্ত্রিত করা সম্ভব। দ্বিতীয়ত, এই বিশ্বাস দ্বারা চালিত হওয়া যে, এটি রহস্যময় ও অতিপ্রাকৃতিক, অতএব কোনো রীতি দ্বারা ্এটি নিয়ন্ত্রণযোগ্য নয়। এই দুই চরম মানসিকতার মাঝে বহুবিধ মধ্যবর্তী দৃষ্টিভঙ্গিও রয়েছে যা মানুষের অনুসৃত পন্থা, আচার-আচরণ ও ফলাফল থেকে আঁচ করা যায়।
ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী মুসলমানদের জীবন নির্বাহে ব্যর্থতা একটি সমস্যা যা সহজেই অনুমেয়। এটি মেনে নিলেও প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে উপরিউক্ত দৃষ্টিভঙ্গির কোন্টি মুসলমানদের পোষণ করা উচিত? বস্তুত এরূপ আলাপ-আলোচনার মাধ্যমেই সচেতনতা সৃষ্টি করলেই মুসলমানরা সমস্যার সমাধানে কোন্ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করবে এবং কোন্টি পরিহার করবে তা নির্ণয়ে সহায়ক হবে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে, দুই দৃষ্টিভঙ্গি গুলিয়ে গিয়ে প্রতিটিই অবান্তর হয়ে গেছে। সুতরাং এর সমাধান বহুলাংশে নির্ভর করে পরিচ্ছন্ন অন্তর্দৃষ্টি উপর।”
সুনান ও সাফল্যের শর্তে
নিচে আমার ও একজন তরুণ মুসলমানদের মধ্যকার সংলাপ তুলে দিলাম। আমি কি তার প্রশ্নের জবাব দিই।
প্রশ্ন: আমরা কি সত্যের অনুসরণ করছি এবং আমাদের বিরোধীরা কি বাতিলের অনুসরণ করছে?
উত্তর: জী, হ্যা।
প্রশ্ন: আমাদের প্রভু কি ওয়াদা করেননি বাতিলের ওপর হক এবং কুফরির ওপর ঈমানের বিজয় হবে?
উত্তর: অবশ্যই, আল্লাহ কখনো তাঁর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না।
প্রশ্ন: তাহলে আমরা কিসের জন্যে অপেক্ষা করছি? আমরা বাতিলের বিরুদ্ধে কেন যুদ্ধ ঘোষণা করি না?
উত্তর: আমাদের ধর্ম শিক্ষা দেয় বিজয়ের জন্য শর্ত ও সুনান আছে। এটা আমাদের মানতে হবে। এই বিবেচনা না থাকলে রাসূলুল্লাহ (সা) মক্কী যুগে প্রথমেই পৌত্তলিকতার বারুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতেন। মূর্তি-অধ্যুষিত হওয়া সত্ত্বেও কা’বায় সালাত আদায় করা তাঁর পক্ষে অসহনীয় মনে হতো। প্রশ্ন: এই সুনান ও শর্ত কি?
উত্তর: প্রথমত, কেবল হক বলেই হক আল্লাহ্ বিজয়ী করেন না। তিনি সৎকর্মশীল লোকদের সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার ফলেই বিজয় দান করেন। কুরআনে পরিষ্কার বলা হয়েছে: “তিনিই তোমাকে স্বীয় সাহায্য ও মুমিনদের দ্বারা শক্তিশালী করেছেন। তিনি তাঁদের পরস্পরের হৃদয়ে প্রীতি স্থাপন করেছেন।” (৮:৬২-৬৩)
প্রশ্ন: কোথায় সেই ফেরেশতা যাঁরা হকের পক্ষে ও বাতিলের বিরুদ্ধে সাহায্যে করেছিলেন-যেমন তাঁরা বদর, খন্দক ও হুয়ানের যুদ্ধে সাহায্য করেছিলেন?
উত্তর: আল্লাহ যখন ইচ্ছে করবেন তখন ফেরেশতারা মুমিনদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসবেন। কিন্তু তাঁরা শূন্যের মধ্যে অবতীর্ণ হবেন না। দুনিয়ায় হকের জন্য সংগ্রামরত সত্যিকার প্রয়োজন হবে এবং যাদেরকে শক্তিশালী করার জন্যে আল্লাহ্র সাহায্যের প্রয়োজন হবে। বদরের যুদ্ধের সময় নাযিলকৃত আয়াত থেকে এটা পরিষ্কার বোঝা যায়: “স্মরণ করো, তোমাদের প্রভু ফেরেশতাদের প্রতি প্রত্যাদেশ করেন: আমি তোমাদের সাথে আছি। সুতরাং মুমিনদের অবিচলিত রাখ। যারা কুফরি করে আমি তাদের হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার করবো। (৮:১২)
প্রশ্ন: সত্যিকার ঈমানদার আছে কি? তাতেই কি বিজয় নিশ্চিত হবে?
উত্তর: তাদেরকে যথাসাধ্য ইসলামের প্রচার চালিয়ে তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করে এমন পর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে যাএ শত্রুর শক্তি সাথে ভারসাম্য সৃষ্টি হয়। একজনের পক্ষে একশ’ বা হাজারেরর বিরুদ্ধে লড়াই করা অযৌক্তিক হবে। কুরআনুল করীমে যে ভারসাম্যের কতা বলা হয়েছে তাতে একজন সত্যিকার মুমিন দশ জনের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে:
“হে নবি! ঈমানদারদেরকে যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করুন। তোমাদের মধ্যে যদি বিশ জন ধৈর্যশীল থাকে তারা দু’শ জনের ওপর জয়ী হবে এবং তোমাদের মধ্যে একশ’ জন থাকলে এক হাজার কাফিরের ওপর বিজয়ী হবে।” (৮:৬৬) প্রশ্ন: কিন্তু আমাদের প্রতিপক্ষ সদা সতর্ক, তারা অন্তর্ঘাতী কৌশলে উৎকর্ষতা লাভ করেছে।
উত্তর: এ থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, এমন একটি অপরিহার্যশর্ত আছে যা ছাড়া বিজয় সুনাশ্চিত হতে পারে না। তা হচ্ছে, বিপদ ও কষ্টে সহিষ্ণুতা ও উস্কানির মুখে দৃঢ়তা। রাসূলুল্লাহ (সা) আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-কে বলেন, “সহিষ্ণুতা বিজয়ের একটি পূর্ব শর্ত।”
আল্লাহ্ পাক স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা)-কে এই উপদেশ দিয়েছেন: “তোমার ওপর যে প্রত্যাদেশ পাঠিয়েছি তুমি তা অনুসরণ করো এবং তুমি ধৈর্য ধারণ করো যে পর্যন্ত না আল্লাহ্র বিধান আসে এবং আল্লঅহ্ই সর্বোত্তম বিধানকর্তা।” (১০:১০৯) অন্য আরকেটি আয়াতে বলা হয়েছে, “ধৈর্য ধারণ করো, তোমার ধৈর্য তো হবে আল্লাহ্রই সাহায্যঅ তাদের দরুন দুঃখ করো না এবং তাদের ষড়যন্ত্রে তুমি মনঃক্ষুণ্ন হয়ো না। আল্লাহ্ তাদেকই সাথে আছেন যারা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং যারা ক্ষমাশীল।” (১৬:১২৭-১২৮)
আল্লাহ্ আরো বলেন: “অতএব তুমি ধৈর্য ধারণ কর, নিশ্চই আল্লহ্র ওয়াদা সত্য। যারা দৃঢ় বিশ্বাসী নয় তারা যেন তোমাকে বিচলিত না করতে পারে।” (৩০-৬০) আল্লাহবলেন: “অতএব তুমি ধৈর্য ধারণ কর যেমন ধৈর্য ধারণ করেছিলেন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ রসূলগণ।” (৪৬-৩৫)
এবং আল্লাহ্ আরো বলেন: ধৈর্য ধারণ কর তোমার প্রভুর আদেশের অপেক্ষায়। তুমি আমার চোখের সামেনই আছ। তুমি তোমার প্রভুর সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর যখন তুমি শয্যা ত্যাগ কর। (৪৬:৩৫)
প্রশ্ন: কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সাফল্য ছাড়া আমরা দীর্ঘদিন কি ধৈর্য ধারণ করতে পারব?
উত্তর: কিন্তু আপনারা কি ইতিমধ্যে একটি অজ্ঞ লোককেও শিখ্ষা দেবেন না, কাউকে কি সৎপথে আনবেন না অথবা কাউকে কি তওবায় অনুপ্রাণিত করবেন না? যখন সে ইতাবচক জবাব দিলো তখন আমি বললাম, এটাই হচ্ছে আমাদের বিরাট সাফল্য যা আমাদেরকে আমাদের লক্ষ্যের কাছাকাছি নিয়ে যাচ্ছে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন: “আল্লহ্ যদি একটি লোককেও তোমার চেয়েও অনেক উত্তম।” তাছাড়া আমাদের কাছে দাওয়াত পৌছানোর ব্যাপারেই কৈফিয়ত চাওয়া হবে, আমরা নিজেরা তাতে সফল হলাম কিনা তা নয়। আমাদেরকে অবশ্যই ভালবাসার বীজ বপণ করতে হবে এবং আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করতে হবে যাতে উত্তম ফসল পাওয়া যায়। আল-কুরআন সবর্ত্রই আমাদের পথ-প্রদর্শক: “এবং বলো, তোমরা আমল করতে থাক। আল্লাহ্ তো তোমাদের কর্যকলাপ লক্ষ্য করবেন এবং তাঁর রাসূল ও মুমিনগণও করবে এবং তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতার নিকট, অতঃপর তিনি তোমরা যা করতে তা তোমাদেরকে জানিয়ে দেবেন।” (৯:১০৫)
চতুর্থ অধ্যায়
মুসলিম তরুণদের প্রতি উপদেশ
‘আলউম্মাহ’ ম্যাগাজিনে প্রকাশিত আমার প্রবন্ধে আমি মুসলিম তরুণ পুনর্জাাগরণের ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিক নিয়ে আলোচনা করেছি। তাতে আমি পরিশেষে দু’টি বিষয়ের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছি।
প্রথম: এই পুনর্জাগরণ একটি স্বাভাবিক ও সুস্থ চেতনার ইঙ্গিতবাহী। এর মাধ্যমে আমরা প্রকৃতি ও মূলের দিকে অর্থাৎ ইসলামের দিকে ফিরে যাচ্ছি। ইসরামই হচ্ছে আমাদের জীবনে প্রথম ও শেষ। এখানেই আমরা বিপদে আশ্রয় নিই, এখানে থেকেই আমরা শক্তি সঞ্চয় করি।
আমাদের সমাজ পূর্ব ও পশ্চিমের কাছ থেকে ধার মতবাদ দিয়ে সমস্যা মাধানের চেষ্টা করেছে। কিন্তু আধ্যাত্মিক ও বৈষয়িক উন্নতিসহ সকল ক্ষেত্রে উন্নয়নের এই চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। ফলে এখন আমাদের জনগণ ইসলামের অনিবার্য সমাধানে বিশ্বাস করে অথাৎ জীবনের সকল ক্ষেত্রে ইসলামী শারীয়াহর বাস্তবায়ন চায়। অতএব এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই যে, মুসলিম তরুণদের সাহস ও দৃঢ় সংকল্প নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে।
দ্বিতীয়: আমাদের কিছু কিছু তরুণের মধ্যে যে গোঁড়ামি রয়েছে তা হিংসা ও হুমকি দিয়ে পরিশুদ্ধ করা যাবে না। আল্লাহ্র দ্বীনের প্রতি এদের নিষ্ঠা ও আন্তরিকতায় আমাদের কোনো সন্দেহ থাকা উচিত নয়। একমাত্র প্রতিকার হচ্ছে সদিচ্ছা ও আন্তরনিকতা নিয়ে তাদের সাথে মেলামেশা করে তাদের মন-মানসিকতা উপলব্ধি করা এবং বুদ্ধিবৃত্তিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে ব্রান্ত ধারনা দূর করতে উদ্যোগী হওয়া।
আমি কেবল আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে মুসলিম তরুণদের এ ব্যাপারে অনেক উপদেশ দিয়েছি। রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন যে, ঈমানদারদের একে অপরের সাথে সর্বদা পরামর্শ করা উচিত এবং ধৈর্যের সাথে সৎকাজের আদেশ দেয়া এবং অসৎ ও অবাঞ্ছিত কাজ থেকে বিরত থাকা। ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনে পুরস্কার লাভের জন্যে এটি আবশ্যকীয় শর্ত। নিচে আমি আরো কিছু উপদেশ দিচ্ছি:
আমরা বিশেষজ্ঞ জ্ঞানের যুগে বাস করছি। জ্ঞানের একটি শাখায় ব্যুৎপত্তির মানে আরেকটি শাখায়ও পারদর্শী হওয়া নয়। যেমন একজন ইঞ্জিনিয়ারের সাথে চিকিৎসা বিষয়ে পরামর্শ করা যায় না অথবা একজন চিকিৎসকের সাথে আইনের পরামর্শ চাওয়া হাস্যকর। অতএব শারীয়ারহর জ্ঞানও সকলের সমান মনে করা ভুল। এটা ঠিক যে, ধর্মীয় জ্ঞানের শ্রেণী বিশেষের একচোটিয়া অধিকার ইসলাম স্বীকার করে না, যেমন খৃস্টানদের যাজক গোষ্ঠী রয়েছে বা হিন্দুদের ব্রাহ্মণবর্গ। কিন্তু ইসলাম ধর্মীয় জ্ঞানের জ্ঞানে বিশেষজ্ঞদের অস্তিত স্বীকার করে যারা কোনোভাবেই একটি বিশেষ গোষ্ঠী, শ্রেণী আ উত্তরাধিকারসূত্রে বংশগত নয়। বাস্তব কারণেই ধর্মীয় ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কুরআন বলেছে: “সকর মুমিনকে এক সাথে অভিযানে বের হওয়া উচিত নয়, তাদের প্রতিটি দলের এক অংশ বহির্গত হয় না কেন, যাতে তারা দ্বীন সম্বন্ধে জ্হান অনুশীলন করতে পারে এবং তাদের সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পারে, যখন তারা তাদের কাছে ফিরে আসবে, যাতে তারা সতর্ক হয়।” (৯:১২২)
কুরআন ও সুন্নাহর যেসব বিষয়ে আমাদের জ্হান নেই তা বিজ্ঞ ও অবিজ্ঞ লোকদের কাছ থেকে শিখতে বলেছে: “তোমার পূর্বে আমি ওহীসহ মানুষই পাঠিয়েছিলাম, তোমরা যদি না জান তবে জ্ঞানীদের জিজ্ঞাসা করো।” (২১:৭)
এবং “যখন শান্তি অথবা শঙ্কার কোন সংবাদ তাদের কাছে আসে তখন তারা তা প্রচার করে থাকে। যদি তারা তা রাসূল অথবা তাদের মধ্যে যারা ক্ষমতার অধিকারী তাদের গোচরে আনত, তবে তাদের মধ্যে যারা তথ্য অনুসন্ধান করে তারা তার যথার্থতা নির্ণয় করতে পারত।” (৪:৮৩)
আরেকটি আয়াতে আল্লাহ্ বলেন, “সর্বজ্ঞের ন্যায় তোমাকে কেউই অবহিত করতে পারে না।” (৩৫:১৪)
রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জানানো হলো যে, একজন আহত ব্যক্তিকে এই ফতোয়া দেয়া হয়েছে যে, অযু ও নামাযের আগে তার গোটা শরীর ধুয়ে ফেলতে হবে, যার ফলে তার মৃত্যু হয়েছে।তখন তিনি বললেন: “তারা তার মৃত্যু ঘটিয়েছে, আল্লাহ্ তাদেরও মৃত্যু ঘটান। সঠিক জানা না থাকলে তাদের কি জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল না?”এটা খুব বেদনাদায়ক যে, কোনো কোনো লোক অযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও জটিল বিষয়েও য়তোয়া দিতে অভ্যস্ত যা অতীত বর্তমান আলিমদের ফতোয়ার বিরোধী। তারা আগের আলিমদেরকে অজ্ঞ বলতেও কসুর করে না। তারা দাবী করে ইজতিহাদের দরজা সকলের জন্যে খোলা। এটা সত্য, কিন্তু ইজতিহাদের কতকগুলো শর্ত আছে যা এদের মধ্যে নেই। আমাদের পূর্ববর্তীরা তো অনেক বিজ্ঞ লোককেও সতর্ক বিবেচনা ছাড়া তাড়াতাড়ি ফতোয়া দেয়ার জন্যে সমালোচনা করেছেন। তারা বলেন, “কিছু কিছু লোক এত দ্রুত ফতোয়া দেয় অথচ তা হযরত উমার (রা)-এর কাছে পেশ করা হলে তিনি বদরের যুদ্ধের অংশগ্রহণকারী সকলের সাথে পরামর্শ করতেন এবং তারা আরো বলেন, “তোমাদের মধ্যে যারা ফতোয়া দেয়ার ব্যাপারে দুঃসাহসী (পাপ করে) দোযখে যাওয়ার ব্যাপারেও।” গভীর জ্ঞানের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তারা জটিল বিষয়ে বিজ্হ ব্যক্তিদের সাথে পরামর্শ করতেন। যেসব ফতোয়া মৌনভাবে দেয়া হতো ইসলামের প্রাথমিক যুগে সেগুলোকে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত বলে মেনে নেয়া হতো। কারো কাছে ফতোয়া চাওয়া হলে তারা পারত পক্ষে বিরত থাকতেন। আবার কেউ কেউ জানেন না বলে এড়িয়ে যেতেন।
উতবান ইবনে মুসলিম (রা) বলেন যে, একবার তিনি ৩০ মাস উমর (রা)-এর সং্গী ছিলেন। সে সময় উমর (রা)-কে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হয় এবং তিনি প্রায়শ বলতেন যে, তিনি জানেন না। ইবনে আবু লায়লা (রা) ১২০ জন সাহাবীর, (এঁদের মধ্যে অধিকাংশই আনসার), সম্পর্কে বলেছেন, “তাঁদের মধ্যে একজনকে জিজ্হেস করা হলে তিনি আরেকজনকে দেখিয়ে দিতেন, তিনিও আরেকজনকে দেখিয়ে দিতেন, তিনিও আরেকজনকে, এভাবে পালাক্রমে চলতো যতক্ষণ না প্রশ্নকর্তা আবার প্রথম ব্যক্তির কাছেই ফিরে যেতো।”
আতা ইবনে আস সাবির (র) বলেন যে, তিনি তার সমসাময়িক অনেককে ফতোয়া দিতে গিয়ে কাঁপতে দেখেছেন। তবিয়ুনদের মধ্যে সাঈদ ইবনে আল মুসাইয়েব (র) - কে কচিৎ ফতোয়া দিতে দেখা গেছে অথচ তিনি ফিকাহতে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন। যদি তিনি অনিচ্ছাকৃতভাবে ভুল করে থাকেন এবং তাদেরকেও রক্ষা করতে যদি তিনি অনিচ্ছাকৃতভাবে ভুল করে থাকেন এবং তাদেরকেও রক্ষা করতে যারা সেই ফতোয়া অনুসরণ করবে। মাযহাব চুষ্টয়ের ইমামগণও অনুরূপ সতর্কতা অবলম্বন করতেন। কোনো ব্যাপারে নিশ্চিত না হলে তারাও বলতেন যে, জানি না। ইমাম মালেক (র) বিশেষভাবে সতর্ক ছিলেন। তিনি বলেন, “কাউকে কোনে বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলে তার ‘জান্নাত ও জাহান্নম’ সম্পর্কে চিন্তা করা উচিত এবং জবাব দেয়ার আগে নিজের পারলৌকিক মুক্তি সর্ম্পকে ভাবা উচিত। ইবনে আল কাসিম (র) ইমাম মালিক (র) -কে বলতে শুনেছেন, “আমি একটা বিষয়ে দশ বছর ধরে গবেষণা করছি কিন্তু এখনো মনঃস্থির করতে পরিনি।” এবনে আবু হাসান (র) বলেন, “মালিককে ২১ টি বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, “তিনি মাত্র দু’টির ফতোয়া দিয়েছিলেন। তারপর বার বার বলেন, ‘আল্লাহ্ ছাড়া কোনো সাধ্য রবা ক্ষমতা নেই।” জ্ঞানের অম্বেষা থেকে তরুণদের নিরুৎসায়িত করা আমার উদ্দেশ্য নয়। দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত জ্ঞান অন্বেষণ করা আমাদের জন্যে ফরয। আমি যা বলতে চাই তা হচ্ছে তাদের জ্হান যতোই হোক, বিশেষজ্ঞদের সাহায্য নিতে তারা বাধ্য। আশ-শারীয়াহর জ্হানে বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা ও উসুল আছে যা জানা ও বোঝার সময় বা উপায় এই তরুণদের নেই।আমি বলতে চাই যারা কলেজে ভালো লেখাপড়া করে তাদেরকে সেটা ছেড়ে দিয়ে আশ-শারীয়ায় বিশেষজ্ঞ হতে হবে এমন প্রবণতা আমি অনুমোদন করি না। আরেকটি বিষয় বুঝতে হবে, এখন বিজ্হানে দক্ষতা অর্জনের জোর প্রতিযোগিতা চলছে। কোনো মুসলমান যদি আল্লাহ্র জন্যে বিজ্হানে বুৎপত্তি অজর্নের সাধনায় নিম্গ্ন হয় সে আসলেই ইবাদত ও জিহাদে অংশ নেয়।
এখানে স্মর্তব্য, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে ওহী নাযিল হওয়ার কালে তাঁর সাহাবীদের
বিভিন্ন পেশা ছিল। তিনি তাদেরকে নিজ নিজ পেশা ত্যাগ করে আসলাম অধ্যয়নের তাগিদ দেননি; অবশ্য তারা বাদে যাদেরকে এরূপ দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল কিংবা যাঁদের এ ব্যাপারে স্বাভাবিক ঝোঁক ছিল। আমার ভয় হয় অনেক হয়তো জনপ্রিয়তা বা নেতৃত্ব লাভের খায়েশ শরীয়ার জ্হানে দখল চাইতে পারে। মানুষকে প্রলুব্ধ করার জন্যে শয়তানের বহু রাস্তা আছে। অতএব আমাদের চিন্তা, উদ্দেশ্য ও কৌশল সম্পর্কে সতর্ক পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আত্মপ্রতারণার ফাঁদে পড়ে আমরা স্বচ্ছ চিন্তাকে যেন আচ্ছন্ন করে না ফেলি। আমাদেরকে সবর্দা কুরআনের এই আয়াত স্মরণ করা উচিত: “কেউ আল্লাহ্কে দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করলে সে পথে পরিচালিত হবে।”(৩:১০১)
যেহেতু জ্হানের প্রতিটি শাখা বিশেষজ্ঞদের দ্বারা পরিচিতি লাভ করে, অতএব তরুণদেরকে সৎ ও গভীর জ্হানের অধিকারী আলিম ও ফকীহদের কাঝ থেকে ধর্মীয় জ্হান হাসিলের উপদেশ দিচ্ছি। তাদের দেয়া ব্যাখ্যা ছাড়া সুন্নাহর ধর্মীয় জ্হানের প্রধান উৎস-জ্ঞানে সমৃদ্ধ হওয়া সম্ভব নয়। তাদেরকে অশ্রদ্ধা করা মূর্খতা ও ঔদ্ধত্য কুরআন-হাদীসে পারদর্শী হতে চান তাদের ইসলামী শিক্ষার ওপর নির্ভর করা যঅয় না। একইভাবে যারা উলামা ও ফুকাহার সিদ্ধান্তকে প্রধান অবলম্বন বানায়, কুরআন ও হাদীসকে উপেক্ষা করে, তাদের জ্হানের অবস্থাও হৃদয়বিদারক!
আবার অনেক আলিম আছেন যারা সরাসরি কুরআন হাদীসে অধ্যয়ন করেননি, কিন্তু ইসলামের ইতিহাস, দর্শন ও পূঁজিবাদ সম্পর্কে বিশেজ্ঞ। কিন্তু এরা অন্যকে শলিয়াহ শিক্ষা দেয়া অথবা ফতোয়া দেয়ার যোগ্য নন, কারণ তারা তাদের ভাষণে-বিবরণে প্রয়শ সত্যের সাথে পুরান, বিশুদ্ধকে শুদ্ধ, সারকে তারা নিজেরাও বোঝান না। এছাড়া যার আমল নেই তার শিক্ষা বা নেতৃত্ব দেয়ার অধিকার নেই। সততা, সাধুতা ও আল্লাহ্র ভীতি হচ্ছে প্রকৃত জ্ঞানের ফল। কুরআনুল কারীম বলছে, “আল্লাহ্র বান্দাদের মধ্যে যারা জ্ঞানী তারাই তাকে ভয় করে।” (৩৫:২৮)
এরূপ সাধুতা ও আল্লাহ্র ভয় একজন আলিমকে মূর্খতাসুলভ কাজ এবং শাসক অথবা সরকারের সেবাদাস হওয়া থেকে বিরত রাখে।
বিজ্হানের তৃতীয় বৈশিষ।ট্য হচ্চে ভারসাম্য। এটা ইসলামেরই অনুপম বৈশিষ্ট্য। দুর্ভাগ্যনকভাবে দু’টি প্রান্তিক প্রবণতা আমাদের রয়েছে: চরমপন্থা, শিরক, অবহেলা, গোঁড়ামি কিংবা বিচ্ছিন্নতা। আল-হাসান আল-বসরী (র) সাবধান করে দিয়ে বলেছেন, “চরমপন্থী উদাসীনদেন কার্যকলাপের দরুন দমৃ হারিয়ে যাবে।” প্রথম পক্ষ মাযহাব মানকবে কিন্তু ইজতিহাদের দরজা রুদ্ধ করে দেবে। দ্বীতিয় পক্ষ মাযহাব অস্বীকার করে তার সকল নীতি খন্ডনে প্রয়াসী হবে। এছাড়া আরেক দল কুরআন-হাদীসের আক্ষরিক অর্থ মেনে চলতে চায়। যা হোক দুই চরমের মাঝে আসল ইসলাম হারিয়ে যায়। অতএব আমাদের দরকান আরসাম্যময় সাধু ও সৎ চরিত্রের অধিকারী ফকীহ যারা সুচিন্তিতভাবে যুগের চাহিদাকে সামনে রেখে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে রায় দেবেন যা সাধারণ মানুষের জন্যে কল্যাণকর হবে। ইমাম সুফিয়ান আস-সাওরী বলেন, “সুস্পষ্ট যুক্তির ভিত্তিতে কোনো কিছুকে বৈধ করা জ্ঞানের পরিচায়ক, আর গোঁড়ামি তো যে কেউ নিষদ্ধ ঘোষণা করতে পারে।”
মুসলিম তরুণদেরকে গোঁড়ামি ও বাড়াবাড়ি পরিহার করতে হবে। একজন মুসলিম ঈমানে-আমলে সতর্ক হবে; কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, ধর্মীয় সহজ বিষয়গুলোকে উপেক্ষা করে ধর্মকে স্রেফ একটি কঠোর সতর্কবাণীতে পরিণতকরবে। কুরআন, সুন্নাহ, রাসূলুল্লাহ (সা) ও তাঁর সাহাবীরা বাড়াবাড়ির বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন; কেননা বাড়াবাড়ি আমলের বিষয়গুলোকে ঈমানদারদের জন্যে কষ্ঠকর করতে পারে। এ প্রসঙ্গে সিয়াম, পাকসাফ, বিবাহ ও কিয়াস সংক্রান্ত কুরআনের আয়াতগুলো লক্ষণীয়: “আর্লাহ্ তোমাদের জন্য যা সহজ তা চান এবং যা তোমাদের জন্য কঠিন তা চান না।” (২:১৮৫)
“আল্লাহ্ তোমাদেরকে কষ্ঠ দিতে চান না।” (৫:৬)
“আল্লাহ্ তোমাদের ভয়ের লঘু করতে চান, মানুষ সুষ্টগতভাবেই দুর্বল।” (৪:২৮) “হে ঈমানদারগণ! নিহতদের ব্যাপারে তোমাদের জন্য কিসাসের বিধান দেয়া হয়েছে। মুক্ত ব্যক্তির বদলে মুক্ত ব্যক্তি, ক্রীতদাসের পরিবর্তে ক্রীতদাস ও নারীর পরিবর্তে নারী। কিন্তু তার ভাইয়ের পক্ষ থেকে কীছুটা ক্ষমা করা হলে যথাযথ বিধির অনুসরণ করা ও সততার সাথে তার প্রাপ্য আদায় বিধেয়। এটা তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে ভার লাঘব ও অনুগ্রহ।”(২:১৭৮)
রাসূলের সুন্নায়ও নমনীয়তা ও ভারসাম্যের পক্ষে ও বাড়াবাড়ির বিরুদ্ধে হুঁশিয়ার করে দেয়া হয়েছে: “ধর্মে বাড়াবাড়ি থেকে সাবধান। তোমাদের পূর্বের (জনগোষ্ঠী) বাড়াবাড়ির জন্যে ধ্বংস হয়ে গেছে। ” (আহমদ, নাসাঈ,ইবনে মাজা) তারা ধ্বংস হয়েছ যারা চুল ছেঁড়াছেঁড়িতে লিপ্ত এবং রাসূলুল্লাহ (সা) এ হাদীসটি তিনবার উচ্চারণ করেন। (মুসলিম)
এছাড়া আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, “একবার এক বেদুঈন মসজিদে প্রস্রাব করেছিল। লোকজন তাকে মারতে গেল, কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা) তাদেরকে আদেশ দিলেন, “তাকে ছেড় দাও (প্রস্রাবের জায়গায়) এক বালতি অথবা এক গামলা পানি ঢেলে দাও। তোমাদেরকে সব কিছু সহজ করার জন্য পাঠানো হয়েছে, কঠিন করার জন্য নয়।” (বুখারী)
এটা সত্য যে, রাসুলূল্লাহ (সা) সব সময় দ’টির মধ্যে সহকটিকে বেছে নিতেন যদি তা পাপ না হয়। যকন জানতে পারেন যে, মুয়াজ (রা) নামায গীর্ঘায়িত করেন, তখন তিনি মুয়াজ (রা) -কে বলেন, “হে মুয়াজক! তুমি কি মানুষকে পরীক্ষা করছ?” (বখারী)
রাসূলুল্লাহ (সা) একথা তিনবার বললেন, “কেউ যদি কঠোরতার মাধ্যমে উৎকর্ষ অর্জনে আগ্রহী হয় তবে সে করতে পারে, কিন্তু অন্যকে বাধ্য করতে পারে না। এটা করতে গিয়ে সে অবচেতনভাবে অন্যকে ধর্ম থেকে সরিয়েও দিতে পারে।” রাসূলুল্লাহ (সা) - এর ওপরেই জোর দিয়েছেন। এজন্যে রাসূলুল্লাহ (সা) একাকী নামায দীর্ঘয়িত করতেন, কিন্তু ইমামাতির সময় সংক্ষিপ্ত করতেন। এ সংক্রান্ত একটি হাদীস ইতিপূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে।
মুসলিম (র) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইমামতির সময় কুরআনের চোট ছোট আয়াত পড়তেন। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) সহিষ্ণুতার নির্দশন হিসেবে একাদিক্রমে রোযা রাখার বিরুদ্ধে সতর্ক করে দিয়েছেন। কিন্তু লোকেরা তাঁকে বলল, “আপনি এরূপ করেন”। তিনি বলেন, “আমি তোমাদের মতো নই, আমার ঘুমের মধ্যে আমার প্রভু আমাকে কাদ্য ও পানীয় দান করেন।” ধর্মীয় বিষয়গুলো সহজরূপে তুলে ধরা এখন আগের চেয়েও বেশি প্রয়োজন। আমরা যে যুগে বাস করছি, সে যুগটি পাপপূর্ণ বস্তুবাদে নিমজ্জিত। এর মধ্যে ধর্মপালন দুঃসাধ্য বটে। এজন্যেই ফুকাহা কঠোরতার পরিবর্তে নমনীয়তার সুপারিশ করেছেন। দাওয়াতী কাজে কি পদ্ধতি আবলম্বন করা দরকার তা আগেই উল্লেখ করেছি। কুরআন বলছে: “তুমি মানুষকে তোমার প্রভুর পথে আহবান কর হিকমত ও সদুপদেশ দ্বারা এবং তাদের সাথে আলোচনা কর সদ্ভাবে।” (১৬:১২৫)
স্পষ্টত উক্ত আয়াতে শুধু মধুর কথা নয় সদয় অভিব্যক্তি কথাও বলা হয়েছে। এই লক্ষ্যে প্রথমে মতানৌক্যে নয়, মতৈনক্যের সূত্র ধরে আলোচনা শুরু করতে হবে। আলকুরআন বলছে: “তোমরা উত্তম পন্থা ব্যতীত আহলে কিতাবদের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয়োনা, তবে তাদের সাথে করতে পার, যারা তাদের মধ্যেসীমাংঘনকারী এবং বলো, আমাদের প্রতি ও তোমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে, তাতে আমরা বিশ্বাস করি এবং আমাদের ইলাহ ও তোমাদের ইলাহ তো একই এবং আমরা তাঁরই প্রতি আত্মসমর্পণকারী। (২৯:৪৬)
কোনো মতানৈক্যের বিষয় থেকে গেলে তা আল্লাহ্ স্বয়ং বিচার করবেন, “যদি তারা তোমার সাথে বিতণ্ডায় লিপ্ত হয় তবে বলো: “তোমরা যা কর সে ব্যাপারে আল্লাহ সম্যক অবহিত। তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করছ কিয়ামতের দিনে আল্লাহ্ পাক সে বিষয়ে তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করবেন।” (২২:৬৮-৬৯)
এই যদি অমুসলমানদের সাথে আচরণের পদ্ধতি হয় তাহলে মুসলমানদের সাথে মুসলমানদের কথাবার্তা কি রকম হওয়া উচিত। আমরা তো অনেক সময় আচার-আচরণে ‘আন্তরিক’ ও কর্কশে’র তফাতও ভুলে যাই। প্রকৃত দাইয়াকে মধুর ভাষণ ও সদয় অভিব্যক্তি দিয়ে দাওয়াতী কাজ চালাতে হবে। এমন প্রমাণ আছে যে, কর্কশ আচরণের ফলে আসল বিষয় বিকৃত বা বিলীন হয়ে গেছে। এগুলো থেকে আমাদের শিক্ষা নেয়া উচিত। এজন্যেই বলা হয়েছে: “যে ভঅল পথের আদেশ করে সে যেন তা ঠিক পথে করে।’
ইমাম গাজ্জালী(র) তাঁর ‘আমরু বিল মারুফ ওয়া নাহি আনিল মুনকার’ বইয়ে লিখেছেন, ‘যে ব্যক্তি ভাল কাজের আদেশ দেয় এবং নিষেধ করে খারাপ কাজ থেকে তার ধৈর্য, সহানুভূতি, জ্ঞান ও প্রজ্ঞা থাকতে হবে।‘ প্রসঙ্গত তিনি একটি ঘটনার উল্লেখ করেন। একবার এক ব্যক্তি খলীফা আল-মামুনের দরবারে এসে কর্কশ ভাষায় পাপ পূর্ণ্য বিষয়ক পরামর্শ দান শুরু করল। ফিকাহ সম্পর্কে আল-মামুনের ভাল জ্ঞান ছিল। তিনি লোকটিকে বললেন, “ভদ্রভাবে কথা বলো। স্মরণ করো আল্লাহ্ তোমার চেয়েও ভাল লোককে আমার চেয়েও একজন খারাপ শাসকের কাছে পাঠিয়েছিলেন এবং তাকে নম্রভাবে কথা বলার আদেশ দিয়েছিলেন। তিনি মূসা (আ) ও হারুন (আ)-কে যারা তোমার ভাল ফিরাউনের- যে আমার চেয়েও খারাপ ছিল-কাছে পাঠিয়েছিলেন এবং তাদেরকে আদেশ দিয়েছিলেন: ‘তোমরা দু’জন ফিরাউনের কাছে যাও, সে সকল সীমালংঘন করেছে, কিন্তু তার সাথে নম্রভাবে কথা বলো। হয়তোবা সে হুঁশিয়ারির প্রতি কর্ণপাত করবে অথবা (আল্লাহ্কে) ভয় করবে।” (২০:৪৩-৪৪)
এভাবে মামুন তর্কে জয়ী হলেন। আল্লাহ্ পাক মূসা (আ)-কে ভদ্র ভাষায় ফিরাউনের কাছ দাওয়াত পেশ করার শিক্ষা দিয়েছন।
মূসা (আ) ও ফিরাউনের মধ্যেকার সংলাপ পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ফিরাউনের ঔদ্ধত্য, নিষ্ঠুরতা ও লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সত্ত্বেও মূসা (আ) অত্যন্ত সতর্কতার সাথে দাওয়াত পেশ করৈছেন। সূরা আশশূরায় এ বিষয়টি লক্ষ্য করা যায়।
রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জীবন ও সুন্নহ অধ্যয়ন করলেও দেখা, মায়া, নম্রতা-সেখানে কর্কশতা ও কঠোরতার কোনো অবকাশ নেই। তাই কুরআন বলছে: “এখন তোমাদের মধ্য বেদনাদায়ক এবং তিনি তোমাদের ব্যাপারে খুবই উদ্বিগ্ন। তিনি ঈমানদারদের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু ও করুণাশীল।” (৯:১২৮)
সাহাবীদের সাথে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে কুরআন বলছে : “আল্লাহ্র দয়ায় তুমি তাদের প্রতি কোমল হৃদয় হয়েছে, তুমি যদি রূঢ় ও কঠোর হৃদয় হতে তাহলে তারা আশপাশ থেকে সরে যেতো।” (৩: ১৫৯)
একদিন একদল ইহুদী এসে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে সম্ভাষণ জানাল, “আস সামু আলাইকুম” যার আক্ষরিক অর্থ ‘আপনার মৃত্যু হোক’। হযরত আয়েশা (রা) ক্রুদ্ধ হয়ে জবাব দিলেন, “আলাইকুমুস সামু ওয়া আলানাহ” অথাৎ “তোমাদেরও মৃত্যু হোক, অভিশপ্ত হও তোমরা।” কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা) কেবর বললেন, ওয়া আলাইকুম (তোমাদের ওপরেও)” তারপর আয়েশা (রা)-কে লক্ষ্য করে বললেন, “যে সকল বিষয়ে দয়া করুণা করে আল্লাহ্ তাকে ভালবাসেন।” (সকল প্রামাণ্য সূত্রে সমর্থিত) তিনি আরো বললেন, দয়া সব কিছু সুন্দর করে। হিংসা সেগুলোকে ত্রুটিপূর্ণ করে।” (মুসলিম)
জুবায়ের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বর্ণনা করেন, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছেন: “যে কোমলতা থেকে বঞ্চিত সে সকল ভাল থেকে বঞ্চিত।” (মুসলিম) সকল ভাল থেকে বঞ্চিত হওয়ার চেয়ে বড় শাস্তি আর কী থাকতে পারে! আশা করা যায়, উপরের উদ্ধৃতিগুলো আমাদের বাড়াবাড়ি পরিহার করে প্রজ্ঞার পথে চালিত হওয়ার জন্যে যথেষ্ট। আমি আরো কয়েকটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই:
ক. মাতাপিতার প্রতি কর্তব্য অবশ্যই পালন করতে হবে। মাতাপিতা, ভাইবোন, কারো সাথেই এই অজুহাতে কর্কশ ব্যবহার করা যাবে না যে, তারা ধর্মের সীমালংঘনকরছে। তারা যদি এরূপ করেও তবুও তাদের সম্মান-স্নেহ পাওয়ার অধিকার ক্ষুণ্ণ হয় না। কুরআনে স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে: “তোমার পিতামাতা যদি তোমাকে পীড়াপীড়ি করে আমার সমকক্ষ দাঁড় করাতে যে বিষয়ে তোমাদর কোন জ্ঞান নেই, তুমি তাদের কথা মেন না। তবে পৃথিবীতে তাদের সাথে সদ্ভাবে বসবাস করবে এবং যে বিশুদ্ধ চিত্তে আমার অভিমুখী হয়েছে তার পথ অবলম্বন কর।” (৩১ “ ১৫)
অনুরূপভাবে পিতা ইবরাহীম (আ)-এর আচরণ থেকেও আমরা শিক্ষা নিতে পারি। কুরআনে এর বর্ণনা আছে। পিতাকে সত্য পথে আনার জন্য তিনি পিতার রূঢ়তা সত্ত্বেও তাকে কোমলতার সাথে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। তাহলে মুসলমান পিতামাতাদের সাথে কিরূপ আচরণ করতে হবে?
খ. সকল মানুষ এক, ইসলাম এই শিক্ষা দেয়। কিন্তু এ সম্পর্কে ভুল ধারণা থাকা উচিত নয়। মানুষে মানুলে অনেক ফার্থক্য আছে। তার মধ্যে বয়স একটি। এজন্যে শিষ্টতা ও সম্মানের দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশি, শাসকের অধিকারের দিকে খেয়াল রাখতে হবে। যবক সম্মান করবে বৃদ্ধকে, ইসলাম এই শিক্ষা দেয়। এ সম্পর্কে অনেক হাদীস আছে। যেমন: “বৃদ্ধ মুসলমানের প্রতি সম্মান আল্লাহ্র গৌরব।” (আবু দাউদ)
এবং “যে ব্যক্তি ছোটদের প্রতি স্নেহ, বৃদ্ধদের প্রতি সম্মান ও জ্ঞানীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না, সে আমার (উম্মতভুক্ত) নয়।” (আহমদ, তাবরানী, হাকিম)
গ. যারা দাওয়াতী কাজে অভিজ্ঞ, এক সময় খুব সক্রিয় ছিলেন, কোনো কারণে এখন ঝিমিয়ে পড়েছেন তাদের প্রতি সদয় দৃষ্টি রাখতে হবে। তাদের অবদানের কথা ভুলে গিয়ে তাদের নিন্দামুখের হওয়া উচিত নয়। এটাও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সুন্নাহ। হাতিব ইবনে আবু বালতাহ (রা) -এর ঘটনা থেকে এই শিক্ষা পাওয়া যায়। তিনি মক্কা বিজয়ের প্রস্তুতি সম্পর্কে খবর সরবরাহের বিনিময়ে মক্কায় অবস্থিত তাঁর পরিবার-পরিজনকে রক্ষার অনুরোধ করে পৌত্তলিক কুরায়েশদের কাছে বার্তা পাঠান। বার্তাটি ধরা পড়লে হাতিব স্বীকার করেন। তখন হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা) তার বিশ্বাসঘাতকতায় এতোই ক্রুদ্ধ হয়ে পড়েন যে, তিনি তার শিরচ্ছেদ করার জন্যে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে অনুরোধ করেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা) তা নাকচ করে দিয়ে বলেন, “তুমি কিভাবে জানো, আল্লাহ্ সম্ভবত বদরের যুদ্ধে অংশগহণকারীদের ভাল কাজ দেখেছেন এবং তাদেরকে বলেছেন: “তোমরা যা খুশী তাই করো। কেননা আমি মাফ করে দিয়েছি তোমাদেরকে (তোমাদের অতীত-ভবিষ্যতের পাপকে)।” প্রাথমিক যুগে হাতিবের ইসলাম গ্রহণ, বদরের যুদ্ধে তার শৌর্যবীর্যের কথা স্মরণ করে রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে ক্ষমা মঞ্জুর করলেন। এভাবে তিনি বদরের যোদ্ধাদের বিশেষ মর্যদা সম্পর্কেও সচেতন করে দিলেন।
ঘ. আমি মুসলিম তরুণদেরকে দিবাস্বপ্ন ও অবাস্তব ভাববাদিতা পরিহার করার উপদেশ দিচ্ছি। তাদেরকে ধূলোর ধরণীতে নেমে বড় বড় শহরের বস্তি ও গ্রামের নিপীড়ত মানুষের সাথে মিশতে হবে। এখানেই নির্ভেজাল পুণ্য, সরলতা ও পবিত্রতার উৎস নিহিত আছে। এসব মানুষ অভাবের তীক্ষ্ণ খোঁচায় দিশেহারা হয় না। এখানে সমাজ পরিবর্তন, পুনর্গঠন ও আন্দোলনের বিপুল উপাদান ছড়িয়ে আছে। এদের সাথে মেলামেশা করে তাদের অশিক্ষা-কুশিক্ষা দূর করে এবং তাদের খারাপ দিকগুলো বর্জন ও সুকৃতির বিকাশে উদ্যেগী হতে হবে। এজন্যে সংঘবদ্ধ ও সম্মিলিত প্রয়াস চাই। নিপীড়িতদের দুঃখ-কষ্ট লাঘব করা এবং তাদেরকে সঠিক পথে এনে জিহাদের কাতারে শামিল করার প্রচেষ্টাও ইবাদাহর মধ্যে গন্য। ইসলামে দাতব্য কাজে উৎসাহ দেয়া হয়, এটি ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত।
আবু হুরায়রাহ (রা) একটি হাদীসে বলেন: “মানুষের প্রতিটি সন্ধির জন্যে সাদাকাহ তার কাছ থেএক প্রাপ্য, প্রতিদিন যখন সূর্য ওঠে। দুই ব্যক্তির মধ্যে মীমাংসা করে দেয়াও সাদাকাহ, পশুর পিঠে চড়তে কাউকে সাহায্য করা অথবা মাল তুলে দেয়াও সাদাকহর অন্তর্ভুক্ত এবং একটি মধুর বচনও সাদাকাহ এবং কল্যণের দিকে প্রতিটি পদক্ষেপ একটি সাদাকাহ, পথ থেকে ক্ষতিকর জিনিস সরানোও সাদাকহ।” (সকল প্রামান্য সূত্রে সমর্থিত)
ইবনে আব্বাস (রা) আরেকটি হাদীসে বলেন, “প্রতিদিন একিট মানুষের প্রতিটি সন্ধির জন্যে তার কাছ থেকে প্রাপ্য।” শ্রোতাদের একজন বলল, “এটা আমাদের জন্যে কুবই কঠিন।” রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, তোমাদের বাল কাজের আদেশ, কারাপ ও অবাঞ্ছিত কাজ থেকে বারণ একটি সালাহ, দরিদ্রের জন্যে সাহায্য একটি সালাহ, রাস্তা থেকে ময়লা সরানোরও একটি সালাহ ও সালাহর পথে তোমার প্রতিটি পদক্ষেপ একটি সালাহ।” (ইবনে খুজায়মা)
বুরায়দা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, “মানুষের ৩৬০ টি অস্থি-সন্ধি আছে। তাকে অবশ্যই প্রতিটির জন্যে সাদাকাহ দিতে হবে।” তারা (সাহাবীরা) বললেন, “হে নবী, এটা কার পক্ষে সম্ভব?” তারা মনে করেছিলেন যে, এটা অর্থনৈতিক সাদাকাহ। রাসূলুল্লাহ (সা) তখন বললেন, “মসজিদে শ্ফেম্মার ওপরে কেউ যদি মাটি চাপা দেয় তাও সাদাকাহ, পথ থেকে বাধা সরানোও সাদাকাহ।” (আহমদ, আবু দাউদ, ইবনে খুজায়মা, ইবনে হাব্বান)
এ রকম তথ্য আরো বহু হাদীসে আছে। অন্ধ, বোবা, দুর্বলের ও দুস্থের প্রতি দয়া প্রদর্শনের উপদেশ রয়েছে এবং এসব কাজকে সাদাকাহ ও ইবদাহ বলে গণ্য করা হয়েছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে মুসলমান সর্বদা পুণ্য কাজের উৎস হিসেবে বিরাজমান। এভাবে অন্যেরও উপকার করছে, নিচের মধ্যেও সদগুণের বিকাশ ঘটাচ্ছে, সেই সাথে অসৎবৃত্তি অনুপ্রবেশের আশঙ্কা থেকে নিরাপদ থাকছে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, “সেই ব্যক্তি রহমতপ্রাপ্ত যাকে আল্লাহ্ সৎকর্মের চাবি এবং অসৎকর্মের তালা বানিয়েছেন।” (ইবনে মাজা)
অবশ্য অনেক ভাববাদী মনে করতে পারেন এতে দাওয়াতী কাজ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আমি মনে করি সামাজিক সম্পর্কটাই একটা বাস্তব দাওয়াহ। এই দাওয়াহ মানুষ আপন পরিবেশে পেয়ে থাকে। ইসলাম কেবল বুলি নয়। দাওয়াহ অর্থ মানুষের সমস্যার সাথে একাত্ম হওয়া, এর প্রতিকারের ব্যবস্থা করা। ইমাম হাসান আল বান্নাহ (র) এ ব্যাপারে সচেতন ছিলেন বলে ইসলামী আন্দোলনের সমাজ সেবা বিভাগ খুলেছিলেন সর্বত্র। তিনি মনে করতেন মুসলমানকে যেমন সালাতের শাধ্যমে ইবদতের তগিদ দেয়া হয়েছে তেমনি তাগিদ রয়েছে দাতব্য কাজেরও। কুরআনুল কারীমে বলা হয়েছে: “হে বিশ্ববাসিগণ, তোমরা রুকু কর, সিজদা কর এবং তোমাদের প্রতিপালকের ইবাদত কর ও সৎকাজ কর যাতে সফলকাম হতে পার এবং জিহাদ কর আল্লাহ্র পথে যেভাবে করা উচিত। তিনি তোমাদেরকে মনোনীত করেছেন। তিনি দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের ওপর কোন কঠোরতা আরোপ করেননি।” (২২ : ৭৭-৭৮)
উপরিউক্ত আয়াত মুসলিম জীবনের ত্রিমুখী ভূমিকার সংজ্ঞা দিয়েছে। আল্লাহ্র সাথে সম্পর্ক হচ্ছে ইবাদতের মাধ্যমে তার সেবা; সামাজিক ভূমিকা হচ্ছে দাতব্য কাজের মাধ্যমে সমাজের সেবা; বাতিল শক্তির সাথে সম্পর্ক হচ্ছে তার বিরুদ্ধে জিহাদ চালানো। এরপরেও হয়তো ভাববাধীরা আগে ভাগে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্টার কথাই বলবে এই যুক্তিতে যে, এটা হয়ে গেলে তো সব সমস্যারই সমাধান অটোমেটিক হয়ে যাচ্ছে। এতে কোনো সন্দেহ নেই ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা তো সমগ্র উম্মাহর দায়িত্ব। এজন্যে তো সময় ও অধ্যবসায় প্রয়োজন। এই প্রিয়তম উদ্দেশ্য অর্জনের পূর্ব পর্যন্ত তো আমাদেরকে সমাজের সেবা ও উন্নতির চেষ্টাও করতে হবে। এই তৎপরতা একাদারে ভবিষ্যত বংশধরদের গঠন, প্রস্তুতি ও উম্মাকে নেতৃত্ব দেয়ার ক্ষমতারও পরীক্ষা। এটা হচ্ছে এই রকম যে, একজনের এক্ষুণি চিকিৎসা দরকার, কিন্তু একজন ইসলামী ডাক্তার ইসলামী রাষ্ট্রের ইসলামী হাসপাতাল ছাড়া রোগীর চিকিৎসা করতে নারাজ। অতএব ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম না হওয়া পর্যন্ত সমাজ বা মানবতার সেবা কিংবা কোনো বিতর্কিত বিষয়ের মীমাংসা স্থাগিত রাখার যুক্তি হাস্যকর।
কাঙ্খিত ইসলামী রাষ্ট্রর রূপ সম্পর্কে আমার ধারণা: একটি জলপাই ও খেজুর গাছের বাগান ফল উৎপাদনমুখী কাজের চেষ্টা না করে জলপাই ও খেজুর ফলনের আশায় বসে থাকবে, এটা কি যুক্তিসঙ্গত? তাকে জীবিকার্জনের জন্যে অন্য কাজও করতে হবে, সেই সাথে কাঙ্খিত ফলের জন্যে জলপাই ও খেজুর গাছেরও যত্ন নিতে হবে।
ঙ. তরুণদের প্রতি আমার সর্বশেষ পিতৃস্নেহসুলভ উপদেশ হচ্ছে: হতাশার শৃংখল থেকে নিজেদের মুক্ত করুন এবং মুসলমানদের মধ্যে নির্মল ও সচ্চরিতের নমুনা হোন। অবশ্য এই আশাবাদের জন্যে আরো কয়েকটি বষয়ে সচেতন র্দৃষ্টি দিতে হবে: প্রথম : মানুষ ফেরেশতা নয়। পিতা আদম (আ) -এর মতো তারাও ভুল করতে পারে। আল-কুরআন আমাদের শিক্ষা দিয়েছে, “আমি তো আগেই আদমের প্রতি নির্দেশ দিয়েছিলাম, কিন্তু তিনি ভুলে গিয়েছিলেন, আমি তাকে সংকল্পে দৃঢ় পাইনি।” (২০ : ১১৫)
মানুষের ভ্রান্তি প্রবণতা ও প্রবৃত্তির প্রতি প্রলোভন স্বীকার করে নিলে আমরা অন্যের ভুলত্রুটির প্রতি সহনীয় ও সহৃদয় মনোভাব পোষণের পাশাপাশি তাদেরকে আল্লাহ্র ক্ষমারও আশা করতে পারব। আল্লাহ্ তায়ালা রাসূলুল্লাহ (সা) - কে উদ্দেশ্য করে বলছেন: “বল, হে আমার বান্দাগণ! তোমরা যারা নিজেদের ওপর যুলুম করেছ, আল্লাহ্র রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না, আল্লাহ্ সকল গুনাহ মাফ করে দেবেন। তিনি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।” (৩৯ : ৫৩)
উক্ত আয়াতে ‘আমার’ বান্দা বলার মাধ্যমে বান্দাদের জন্যে আল্লাহ্র উদ্বেগ ও দয়ার চিত্রই ফুটে উঠেছে।
দ্বিতীয় : এটা বোঝা আবশ্যক যে, মানুষের মনের গহীনে কী আছে তা আল্লাহ্ ছাড়া কেউ আর জানেন না। অতএব তার বক্তব্যের আলোকে তাকে বিচার করতে হবে। তাই কেউ যদি কালিমা পাঠ করে তাহলে তাকে মুসলমান হিসেবেই গণ্য করা উচিত। এটাও রাসূলুল্লাহ (সা) এর সুন্নাহ। তিনি বলেন “আমি আদেশ প্রাপ্ত হয়েছি (আল্লাহ্র দ্বারা ) সেই সব লোকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার যতোক্ষণ না তারা স্বীকার করবে যে, আল্লাহ্ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই এবং মুহাম্মাদ (সা) আল্লাহ্র রাসূল এবং সুচারুরূপে নামায পড়াবে, যাকাত দেবে। তারা সকলে যদি এরুপ করে তারা আমার কাচ থেকে (ইসলামী আইন প্রদত্ত শাস্তির বিধান ব্যতীত) জীবন ও সমাজ রক্ষাকরে এবং আল্লাহ্ তাদের হিসাব নেবেন।”
এ কারণেই তিনি মুনাফিকুনকে শাস্তি দেননি অথচ তিনি নিশ্চত ছিলেন যে, তারা তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত করছে। তাদেরকে হত্যা করার পরামর্শ এলে তিনি বলেন: “আমি ভয় করি লোকে বলবে যে, মুহাম্মদ (সা) তাঁর সাহাবীদের হত্যা করে।”
তৃতীয়: আমাদেরকে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের ওপর বিশ্বাস করে, সে যতো খারাপ করুক একেবারেই জন্মগতভাবে ভালোশূন্য হতে পারে না। বড় ধরনের পাপ করলে সে একেবারে ঈমানশূন্য হয়ে যায় না যতোক্ষণ না সে ইচ্ছাকৃত আল্লাহ্ কে অস্বীকার করে ও তাঁর আদেশ অবজ্ঞা করে। রাসূলুল্লাহ (সা) পাপাচারীকে চিকিৎসার দৃষ্টিতে দেখতেন যমন রোগীকে দেখা হয়। পুলিশের মতো তিনি অপরাধীকে দেখতেন না। ইনশাআল্লাহ নিচের ঘটনা থেকে বিষয়টি পরিস্কার হয়ে যাবে :
একজন কোরায়শী যুবক একদিন রাসূল্লাহ (সা)- এর কাছে এসে ব্যভিচারের অনুমতি চাইল। সাহাবীরা ক্রদ্ধ হয়ে তাকে শাস্তি দিতে উদ্যত হলেন; কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা) -এর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। শান্ত সমাহিত চিত্তে তিনি যুবকটিকে তার আরো কাছে আসতে বললেন। তারপর বললেন, “তুমি কি তোমার মায়ের জন্যে এটা (ব্যভিচার) মেনে নেবে?” যুবকটি জবাব দিল, “না।” রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, “(অন্য) লোকেরাও এটা তাদের জন্যে অনুমোদন করবে না।” অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) বারবার তাকে জিজ্ঞেস করলেন সে তার কন্যা, বোন ও চাচীর জন্যে অনুমোদন করবে কিনা? প্রতিবারই যুবক বলল, “না।” এবং প্রতিবারই রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, “(অন্য) লোকেরাও এটা তাদের জন্য অনুমোদন করবে না।” তারপর তিনি যুবকটির হাত ধরে বললেন, “আল্লাহ্ তার (তরুণের পাপ মার্জনা করুন, তার অন্তর পবিত্র করুন এবং তাকে সহিষ্ণু করুন (তার এই কামনার বিরুদ্ধে)।” (আহমদ, তাবরানী) এই সহৃদয় অনুবুতি সুস্পষ্ট সদিচ্ছা ও মানুষের জন্মগত সুমতির প্রতি আস্থার পরিচায়ক যা মানুষের খারাপ বৃত্তিগুলোকে বিদূরিত করতে সক্ষম। আর খারাপ প্রবৃত্তি ক্ষনস্থায়ী। সুতরাং তিনি ধৈর্যের ও যুক্তির সাতে তার সাথে আলাপ করে তার ভুল চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন। চরমপন্থীরা যুক্তি দেখাতে পারে যে, যুবকটি যেহেতু ব্যভিচার করেনি তাই তার প্রতি উদারতা দেখানো হয়েছে। তাহলে আরো একটি উদাহরণ দেখা যাক : এক মহিলা ব্যভিচারিণী গর্ববতী হয়ে রাসূলূল্লাহর (সা) - এর কাছে এসে দোষ স্বীকার করে তাকে পাথর ছুঁড়ে মেরে ফেলে পাপমুক্ত করার জন্যে বারবার চাপ দিতে লাগলো। তাকে পাথর মারার সময় খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রা) তাকে অবভিশাপ দিচ্ছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে বললেন, “খালিদ নম্র হও। যাঁর হাতে আমার জীবন তাঁর শপথ, সে এমন অনুশোচনা করেছে যে, এমনকি একজন দোষী খাজনা আদায়কারীও যদি অনুতপ্ত হতো তবে তাকেও ক্ষমা করা হতো।” (মুসলিম ও অন্যান্য)
কেউ কেউ যুক্তি দেখাবেন মহিলাটি পাপ করেই অনুতাপ করেছে। তাহলে আরো একটি উদাহরণ দিচ্ছি: রাসূলুল্লাহ (সা)- এর জীবদ্দশায় একজন মদ্যপায়ীকে বার বার রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে আনা হলো এবং বার বার তাকে শাস্তি দেয়া হলো, কিন্তু সে নেশা করতেই তাকলো। একদিন যখন তাকে একই অভিযোগে আবার হাযির করে তাকে বেত্রাঘাত করা হলো তখন এক ব্যক্তি বললো, “আল্লাহ তাকে অবিশপ্ত করুন! কতোবার তাকে শাস্তি দেয়ার জন্যে আনা হলো?” রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, “তাকে অভিশাপ দিও না, আল্লাহ্র শপথ, আমি জানি সে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুলকে ভালবাসে। রাসূলুল্লাহ (সা) আরো বলেন, “তোমার ভাইয়ের বিরুদ্ধে শয়তানকে সাহায্য কোর না।” রাসূরুল্লাহ (সা) তাদেরকে অবিশাপ দেয়া থেকে বারণ করলেন এ কারণে যে, এতে ঐ মানুষটি এবং তার মুসলিম ভাইয়ের মধ্যে মনোমালিন্য ও রেষারেষি সৃষ্টি করতে পারে কারণ-তার পাপ তাকে মুসলিম ভ্রাতৃত্বের বন্ধন থেকে বিচ্ছিন্ন করেনি। উপরিউক্ত ঘটনাবলী গভীরভাবে চিন্তা করলে আমরা বুঝতে পারব যে, মানুষের অন্তর্নিহিত সুকৃতির প্রতি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কী গভীর অন্তর্দৃষ্টি ছিল। অতএব যেসব চরমপন্থীরা কেউ ভুল করলেই তাকে নির্বিচারে কুফর-শিরকের ফতোয়া দেয়, তা তাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞতাপ্রসূত। একজন জ্ঞানী ব্যক্তি একদা বলেছিলেন : “অন্ধকারকে অভিশাপ দেয়ার পরিবর্তে রাস্তায় একটি মোমবাতি জ্বালানোর চেষ্টা করো।”
এই হচ্ছে আমার প্রিয় তরুণ মুসলমানদের প্রতি উপদেশ। আমার উদ্দেশ্য কুরআনুল কারীমে বর্ণিত হযরত শুয়াইব (আ) -এর ভায়ায় : ‘আমি আমার সাধ্য মতো সংস্কার করতে চাই। আল্লাহর মদদেই কিন্তু কাজসম্পন্ন হয়; আমি তাঁরই উপর নির্ভর করি এবং আমি তাঁরই অভিমুখী। (১১ : ৮৮)
পরিভষা সঙ্কেত
১. কিসা : সমতার আইন।
২. আস-সাহীহ : ছয়টি সহীহ হাদীস সংকলনের যে কোন একটি।
-- সমাপ্ত --
সুচীপত্রঃ
লেখকের কৈফিয়ত
অভিযোগ ও বাস্তবতা
ধর্মীয় চরমপন্থার ত্রুটি
ধর্মীয় চরমপন্থার ধারণা
চরমপন্থার লক্ষণ
চরমপন্থার কারণ
১. ছোট খাট বিষয় নিয়ে মেতে থাকা
২. নিষেধাজ্ঞা নিয়ে বাড়াবাড়ি
৩. ভ্রান্ত ধারণা
৪. রূপকের ওপর গুরুত্ব প্রদান
৫. বিশেষ জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা
৬. ইতিহাস, বাস্তবতা ও আল্লাহর সুনান সম্পর্কে সচেতনতার অভাব
৭. দু’টি গুরুত্বপূর্ণ
৮. মুসলিম দেশ থেকে ইসলামের নির্বাসন
৯. ইসলামী দাওয়াতে প্রতিবন্ধকতা
চরমপন্থার প্রতিকার
২. জ্ঞান, মূল্যবোধ ও কর্ম
৩. অন্যের প্রতি সহৃদয় অনুভূতি
৪. আল্লাহর সৃষ্টি রীতির জ্ঞান
মুসলিম তরুণদের প্রতি উপদেশ
লেখকের কৈফিয়ত
অভিযোগ ও বাস্তবতা
ধর্মীয় চরমপন্থার ত্রুটি
ধর্মীয় চরমপন্থার ধারণা
চরমপন্থার লক্ষণ
চরমপন্থার কারণ
১. ছোট খাট বিষয় নিয়ে মেতে থাকা
২. নিষেধাজ্ঞা নিয়ে বাড়াবাড়ি
৩. ভ্রান্ত ধারণা
৪. রূপকের ওপর গুরুত্ব প্রদান
৫. বিশেষ জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা
৬. ইতিহাস, বাস্তবতা ও আল্লাহর সুনান সম্পর্কে সচেতনতার অভাব
৭. দু’টি গুরুত্বপূর্ণ
৮. মুসলিম দেশ থেকে ইসলামের নির্বাসন
৯. ইসলামী দাওয়াতে প্রতিবন্ধকতা
চরমপন্থার প্রতিকার
২. জ্ঞান, মূল্যবোধ ও কর্ম
৩. অন্যের প্রতি সহৃদয় অনুভূতি
৪. আল্লাহর সৃষ্টি রীতির জ্ঞান
মুসলিম তরুণদের প্রতি উপদেশ

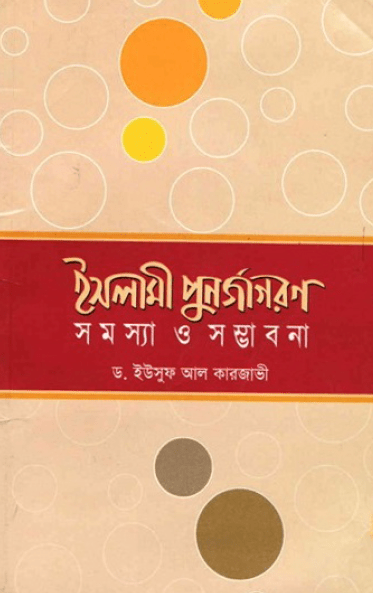 স্ক্যান কপি ডাউনলোড
স্ক্যান কপি ডাউনলোড