অনুবাদকের কথা
আল্লামা ইউসুফ আল-কারযাভী লিখিত আরবী গ্রন্থ ‘আল-হালাল ওয়াল হারাম ফিল ইসলাম’- এর বাংলা অনুবাদ ‘ইসলামের হালাল-হারামের বিধান’ বাংলাভাষী সুধীমণ্ডলীর কাছে উপস্থিত করতে পেরে আমি আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহ তা’য়ালার শোকর আদায় করছি। এ নগণ্য ব্যক্তিকে আল্লাহ তা’য়ালা আল্লামা কারযাভী লিখিত ‘ফিক্হুয্-যাকাত’-এর দুইটি বিরাট খন্ডের বাংলা অনুবাদ ইতিপূর্বে পেশ করার তওফীক দিয়েছেন। সেজন্যে শোকর আদায় করার মতো ভাষা আমার জানা নেই।
বস্তুত ইউসুফ আল-কারযাভী বর্তমান শতাব্দীর একজন শ্রেষ্ঠ ইসলামী ফিকাহ্বিদ- একথা শুধু আমার নয়, একালের বহু বিখ্যাত মনীষীই তা অকপটে স্বীকার করেছেন। তা যেমন তাঁর লিখিত সব কয়টি বড় বড় ও গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ অকাট্যভাবে প্রমাণ করে, তেমনি বাংলা ভাষায় প্রকাশিত ‘ইসলামের যাকাত বিধান’-এর দুইটি খণ্ড ও তাঁর লিখিত অমর গ্রন্থ ‘আল ঈমান ওয়াল হায়াত’ অবলম্বনে আমার লিখিত ‘উন্নত জীবনের আদর্শ’ও পাঠকদের কাছে নিঃসন্দেহ করে তুলেছে।
গ্রন্থকারের বর্তমান গ্রন্থখানিও যেমন ব্যাপক আলোচনাপূর্ণ তেমনি এর তুলনা দুনিয়ার আরবী, উর্দু ও অন্যান্য কোন ভাষায়ই খুঁজে পাওয়া যাবে না। গ্রন্থকার নিজেই বলেছেনঃ হালাল-হারাম বিষয়ে এ গ্রন্থখানি বিশ্ব ইসলামী সাহিত্যে সর্বোচ্চ সংযোজন। গ্রন্থকারের এ দাবি যে একশ’ ভাগ সত্য, তা এর পাঠক মাত্রই স্বীকার করবেন। আলোচ্য বিষয়ের বিভিন্ন অংশ ফিক্হ’র কিতাবসমূহে বিচ্ছিন্নভাবে পড়ে রয়েছে, কিন্তু তা প্রাচীন পদ্ধতিতে লেখা বলে আধুনিক কালের লোকদের পক্ষে তা থেকে বক্তব্য উদ্ধার করা কঠিন। একটি নির্দিষ্ট শিরোনামে পূর্ণ ব্যাপকতা, যৌক্তিক মানে ও আধুনিক গবেষণা ও বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়ই এই প্রথমবার একত্রে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। ফলে গ্রন্থখানি গুরুত্বপূর্ণ ইসলামী বিষয়াদির ‘বিশ্বকোষ’ হওয়ার মর্যাদা অর্জন করেছে। এ কারণেই সারা দুনিয়ার মনীষীগণের কাছে বিশেষভাবে সমাদৃত হয়েছে। এর মূল আরবী গ্রন্থের বহু কয়টি সংস্করণ প্রকাশ এবং তুর্কী ও ইংরেজী ভাষায় এর অনুবাদ প্রকাশ ও তার বিপুল চাহিদা এ কথা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে।
গ্রন্থখানিতে আলোচিত বিষয়াবলীর গুরুত্ব অনস্বীকার্য। তওহীদ ও রিসালাত-এর সাথে সাথে হালাল-হারামের মাস্লাসমূহ সমানভাবে মৌলিক গুরুত্বের অধিকারী। হালাল-হারামের পার্থক্য ব্যতীত না ঈমান ও ইসলাম গ্রহণযোগ্য হতে পারে, না কোন ইবাদতই আল্লাহ্র কাছে একবিন্দু কবুল হতে পারে। আমি মনে করি, হালাল-হারাম এর পার্থক্য রক্ষা করে না চললে মানুষের মনুষ্যত্ব রক্ষা পেতে পারে না বরং মানুষের পশুর স্তরে নেমে যাওয়া অবধারিত। গ্রন্থকার পূর্ণ ব্যাপকতা সহকারে বিষয় সংশ্লিষ্ট সকল দিক ও সকল শাখা-প্রশাখা সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা উপস্থাপিত করেছেন সুস্পষ্ট ও অকাট্য দলিল-প্রমাণের ভিত্তিতে।
এ গ্রন্থে আলোচিত বিষয়গুলো এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, বর্তমান বিশ্বের প্রায় সকল ইসলামী চিন্তা কেন্দ্রসমূহে এ সম্পর্কে ব্যাপক অনুসন্ধান কার্য চালানো হচ্ছে। এক কথায় বললে বলা যায়, এসব হচ্ছে আধুনিক মনের জিজ্ঞাসা এবং গ্রন্থ সেই আধুনিক জিজ্ঞাসারই সুস্পষ্ট ও পূর্ণাঙ্গ জবাব। এসব বিষয়ে আরও বহু ইসলামী চিন্তাবিদ গবেষণা চালিয়েছেন, কিন্তু এ গ্রন্থকার যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে উচ্চমানের ব্যাপক তত্ত্ব ও তথ্যভিত্তিক গবেষণার ফসল উপস্থাপিত করেছেন, তা দৃষ্টান্তহীন বললেও অত্যুক্তি হবে না। তিনি চিন্তা ও বিবেচনা ও অগ্রাধিকার দানের ক্ষেত্রে পূর্ণ ভারসাম্য রক্ষা করেছেন, যা অনেকের পক্ষেই সম্ভব হয় না।
গ্রন্থখানির এ উচ্চমানতার দিকে লক্ষ্য করেই আমি এর অনুবাদ করেছি। আমি মনে করতে পারছি যে, দ্বীন-ইসলামের সম্পূর্ণ পূর্ণাঙ্গ ও ব্যাপক আদর্শ বাঙলা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষিত সমাজের কাছে উপস্থাপনের যে কঠিন দায়িত্ব আমার উপর অর্পিত, বর্তমান গ্রন্থখানি সেই দায়িত্ব পালন পর্যায়ে এক মহান সংযোজন। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ এ বিরাট গ্রন্থখানি প্রকাশ করেও সেই দায়িত্ব পালন করছে। এ গ্রন্থে গৃহীত সব কয়টি সিদ্ধান্তে অনুবাদকের সম্পূর্ণরূপে একমত হওয়ার কোন শর্ত অবশ্যই নেই।
মুহাম্মাদ আবদুর রহীম
১ মে, ১৯৮৪ ইং
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
গ্রন্থকারের ভূমিকা
ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে গ্রন্থ প্রণয়নের উদ্দেশ্যে মিসরের জামে আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থিত ইসলামী সংস্কৃতি কেন্দ্রে একটি পরিকল্পনা গ্রহীত হয়। বিশেষ করে ইউরোপ ও আমেরিকায় বসবাসকারী মুসলিম ও অমুসলিমদের সম্মুখে ইসলামের আদর্শ ও শিক্ষার ব্যাপক ও পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা উপস্থাপিত করাই এ পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত। এ মহতী পরিকল্পনায় কার্যত অংশগ্রহণের জন্যে জামে আযহার কর্তৃপক্ষই আমাকে আহ্বান জানিয়েছিলেন।
সন্দেহ নেই, গ্রন্থ প্রণয়ন সংক্রান্ত এ পরিকল্পনা অত্যন্ত মূল্যবান এবং আদর্শিক দৃষ্টিকোণ থেকে এর প্রয়োজনীতা অপরিসীম। এ ধরণের একটি পরিকল্পনা নিয়ে বহু পূর্ব থেকে কাজ করা আবশ্যক ছিল। কেননা বস্তুতই ইউরোপ-আমেরিকায় বসবাসকারী মুসলিম জনগণ ইসলাম সম্পর্কে খুব সামান্যই জানেন। আর সে সামান্য জ্ঞানও নানাবিধ বিকৃতি ও সংশয়ে জর্জরিত। এরই কাছাকাছি সময়ে আমার এ আযহারী বন্ধু আমেরিকা পরিভ্রমণ করে আমাকে লিখলেন যে, এসব দেশে বসবাসকারী বিপুল সংখ্যক মুসলিম মদ্য ব্যবসা ও পানশালা (Bar) চালিয়ে বিপুল অর্থ উপার্জন করছে। কিন্তু মুসলিমদের জন্যে এ কাজ যে সম্পূর্ণ হারাম ও কঠিন গুনাহ, সে বিষয়ে এদের একবিন্দু চেতনা নেই।
তিনি আরও লিখেছেন, মুসলিম পুরুষরা খ্রীস্টান ও ইয়াহূদী- এমনকি নাস্তিক, পৌত্তলিক, মূর্তিপূজারী (Heathen, Idolater)-দের কন্যা স্ত্রীরূপে গ্রহণ করছে, মুসলিম কন্যাদের বিয়ে করতে প্রস্তুত হচ্ছে না।
আর মুসলিমদের অবস্থা যখন এই, তখন অমুসলিমদের অবস্থা কি হতে পারে, তা বলাই নিষ্প্রয়োজন। তারা তো ইসলামের একটা বাহ্যিক বীভৎস রূপই দেখতে পাচ্ছে। ইসলামের অন্তর্নিহিত প্রকৃত সত্য ও সৌন্দর্যের সাথে পরিচিত হওয়ার কোন সুযোগই তারা পাচ্ছে না। ফলে তারা ইসলামের ও মুসলিমদের (মুসলিম হওয়ার দাবিদারদের) প্রতি সকল শ্রদ্ধা-ভক্তি নিঃশেষে হারিয়ে ফেলছে। বিশেষ করে ইসলামের দুশমন খ্রীস্টান মিশনারীরা ও হিংসুক সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোই তাদের সামনে ইসলামের এ বিকৃত চেহারা তুলে ধরে আসছে আবহমান কাল থেকে। এ জন্যে তারা দিনরাত অত্যন্ত হীন চক্রান্ত চালিয়ে যাচ্ছে আবহমান কাল থেকে। অথচ দুনিয়ার মুসলিম চিন্তাবিদগণ এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ অচেতন ও অনবহিত হয়ে রয়েছেন।
তাই এক্ষণে যদি আমাদের চিন্তাবিদদের চেতনা জেগে থাকে ও এ মহতী কার্যক্রমের পরিকল্পনা নেয়া হয়ে থাকে, তবে তা অত্যন্ত মুবারক ও সময়োপযোগী হয়েছে, যা ব্যাখ্যা করে বলার প্রয়োজন হয় না। এ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন এবং ইসলামী দাওয়াতের এ মহামূল্য কাজে সর্বপ্রকার সাহায্য ও সহযোগিতা মুসলিম মাত্রেরই কর্তব্য, তাতেও কোন সন্দেহ নেই। এ কাজ কেবল যে ‘জামে আযহার’ (আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়) কেন্দ্রিক হওয়া উচিত তা-ই নয়, তা তার বাইরে সমগ্র মুসলিম জাহানেও হওয়া বাঞ্ছনীয় বলে আমি মনে করি।
উক্ত ইসলামী সংস্কৃতি কেন্দ্র থেকে এ গ্রন্থকারকে একখানি গ্রন্থ রচনা করতে বলা হয়। তার শিরোনাম দেয়া হয়ঃ ‘আল হালাল ওয়াল হারাম ফিল ইসলাম’- ইসলামে হালাল হারামের বিধান।
সেই সঙ্গে বলে দেয়া হয় যে, গ্রন্থখানি যেন বিস্তারিত আলোচনা-সম্বলিত ও সহজবোধ্য ভাষায় রচিত হয় এবং তাতে দুনিয়ার অন্যান্য ধর্মমত ও সাংস্কৃতির দৃষ্টিকোণের সাথে তুলনামূলক আলোচনা পেশ করা হয়।
প্রথম দৃষ্টিতে ‘হালাল-হারাম’ বিষয়টি যদিও সহজ মনে হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিষয়টি অত্যন্ত জটিল। বিশেষত এজন্যেও যে, এ বিষয়ের ওপর দ্বীনী সাহিত্যে এখন পর্যন্ত কোন গ্রন্থ লিখিত হয় নি, না প্রাচীনকালে, না আধুনিক কালে। বিষয়টির উপকরণসমূহ যদিও তাফসীর, হাদীস ও ইসলামী ফিকাহ্র বিস্তারিত অধ্যায়সমূহে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে রয়েছে এবং পাঠকগণ সেসব অধ্যয়নকালে বিভিন্ন পর্যায়ে তার সাথে পরিচিত হন, কিন্তু সে সমস্ত উপকরণ একখানি গ্রন্থে একত্রে সন্নিবেশিত করা কিছুমাত্র সহজ কার্য নয়।
তা ছাড়া বিষয়টি এমন যে, লেখককে এমন বহু ব্যাপারেই একটা চূড়ান্ত ও নিজস্ব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়, যেসব ব্যাপারে প্রাচীনকালের মনীষীদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে। উপরন্তু সেসব বিষয় মুহাদ্দিসদের রায় সর্বতোভাবে এক এবং অভিন্নও নয়। আর হালাল-হারামের ব্যাপারে বিভিন্ন মতের মধ্য থেকে একটি মাত্র মতকে অগ্রাধিকার দিতে হলেও বিস্তারিতভাবে আলোচনা-পর্যালোচনা করতে হয়। শুধু তাই নয়, এ পর্যায়ের আলোচনায় আলোচনাকারীকে ঐকান্তিক নিষ্ঠা সহকারে সত্যের সন্ধানে আত্ননিয়োগ করতে হয় এবং সেজন্যে প্রাণপণ পরিশ্রম করাও অপরিহার্য হয়ে পড়ে।
ইসলাম বিষয়ে একালের লেখক, গবেষক ও গ্রন্থকারদের দুভাগে ভাগ করা যায়ঃ
এক ভাগের লোকদের সম্পর্কে বলা যায়, পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সাংস্কৃতির চাকচিক্যে তাদের চোখ ঝলসে গেছে। শুধু তাই নয়, পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সাংস্কৃতিকে তাঁরা এক বিরাট দেবতারূপেই গণ্য করেছেন। তার প্রতি তাঁরা পূর্ণ আনুগত্য জানিয়ে তারই পূজা, উপাসনা ও আরাধনায় নিমগ্ন হয়েছেন। তাঁরা সে দেবতার সম্মুখে পূজার উপাচার ও ভেট-উপঢৌকনও পেশ করছেন একনিষ্টভাবে। তার সম্মুখে এঁদের দৃষ্টি ভীত-সন্ত্রস্ত ও অবনত হয়ে আছে। তাঁরা পাশ্চাত্য-সভ্যতা-সংস্কৃতি উৎসারিত সব কিছুকেই চূড়ান্ত সত্য ও চিরকালীন অনুসরণীয় মনে করে নিয়েছেন। তার সাথে মতবিরোধ করতে বা তা থেকে ভিন্নতর মত গ্রহণ করতে ও বিপরীত মতকে খণ্ডন করতে তাঁরা আদৌ প্রস্তুত নন। এ পর্যায়ে কোন বিষয়ের সাথে যদি মিল ঘটে যায়, তাহলে তাঁরা উল্লসিত স্বপ্নে চিৎকার করে উঠেন। আর যেখানেই বৈপরীত্য পরিলক্ষিত হয়, সেখানেই কোন-না-কোনরূপে সামঞ্জস্য বা সমন্বয় সাধনে ব্রতী হন অথবা ইসলামের দিক দিয়ে কৈফিয়তের সুরে কথা বলতে শুরু করেন কিংবা ইসলামের দৃষ্টিকোণকে বিকৃতি করে এমন একটা ব্যাখ্যা পেশ করেন, যার সাথে ইসলামের আদৌ কোন মিল নেই। তাতে তাদের এ ধারণাই প্রকট হয়ে উঠে যে, পাশ্চাত্য সভ্যতা-সংস্কৃতি ও দর্শনের বিরুদ্ধে ইসলামের যেন কিছু বলবার নেই। প্রতিকৃতি, ছবি, প্রতিমূর্তি, জীবের ভাস্কর্য, সুদী ব্যবসায় ও ভিন্ন স্ত্রীলোকের সাথে নিভৃত নিবিড় সাক্ষাতকার, নারীদের নারীত্ব থেকে বিদ্রোহ এবং পুরুষদের স্বর্ণ-রৌপ্যের ভূষণ বা অলঙকারাদির ব্যবহার প্রভৃতি বিষয়ে তাদের বক্তব্য থেকে আমি এ মনোভাবেরই স্পষ্ট পরিচিতি আঁচ করতে পেরেছি। ইসলামে তালাক ও এক সঙ্গে একাধিক স্ত্রী গ্রহণের যে অনুমতি রয়েছে, সেক্ষেত্রেও তাদের মনোভাব কিছুমাত্র ভিন্নতর নয়। মনে হচ্ছে, তাদের বিশ্বাস, পাশ্চাত্য যা হালাল করেছে তা অবশ্যই হালাল, যা হারাম করেছে তা অবশ্যেই হারাম হবে অথচ ইসলাম একটা স্বতন্ত্র জীবন দর্শন, তা মহান আল্লাহ্র নাযিল করা বিধান আর আল্লাহর বিধানই সর্বোপরি ও সর্বজয়ী হবে, এটাই বাঞ্ছনীয়। ইসলামকেই অনুসরণ করতে হবে, তা কাউকে বা অন্য কিছুকে অনুসরণ করতে পারে না- একথা তারা সম্পূর্ণরূপে ভুলে গেছেন। আল্লাহ্ই হচ্ছেন মাবুদ আর সব বান্দা। মাবুদ কখনই বান্দাকে অনুসরণ করতে, তার অধীন হয়ে থাকতে রাজী হতে পারেন না। স্রষ্টা কোন্ কারণে সৃষ্টি কাছে নতি স্বীকার করবেন? আল্লাহ নিজেই বলেছেনঃ
............ (আরবী)..............
প্রকৃত সত্য- মহান আল্লাহ-যদি লোকদের খামখেয়ালীর অনুসরণ করে চলে, তাহলে তো নভোমণ্ডল, পৃথিবী ও তাতে যা কিছু রয়েছে তা সব কিছুই কঠিনভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে।
............ (আরবী)..............
বল, তোমরা আল্লাহর সাথে যাদের শরীক করছ, তাদের মধ্যে কেউ কি পরম সত্যের পথ প্রদর্শন করে। আর বল, যিনি পরম সত্যের পথ প্রদর্শন করেন তিনি অনুসৃত হওয়ার বেশি অধিকারী, না যা আদৌ কোন পথ দেখায় না- তাকেই বরং পথ দেখাতে হয়,- এ ব্যাপারে সে-ই বেশি অধিকারসম্পন্ন।
এ হচ্ছে লেখক গ্রন্থকারদের এক শ্রেণী সম্পর্কিত কথা। আর দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকেরা তো হালাল হারামের বিষয়ে একটা নির্দিষ্ট মতের ওপর অবিচল হয়ে রয়েছে। এ ব্যাপারে তাঁরা হয়ত কোন কিতাবের ভাষ্যের ওপর নির্ভর করেছেন অথবা ধারণা করেছেন ওটাই ইসলাম হবে। ফলে তাঁরা তাঁদের বদ্ধমূলক ধারণা থেকে একবিন্দু সরে দাঁড়াতেও প্রস্তুত নন। এমন কি, এ বিষয়ে শরীয়াতের দলিল-প্রমাণের পরীক্ষা-পর্যালোচনা করে দেখতেও তাঁরা সম্পূর্ণ নারাজ অথচ স্বমত ও ভিন্ন মতের দলিল-প্রমাণসমূহ তুলনামূলকভাবে পরীক্ষণ ও আলোচনা-পর্যালোচনা করলেই প্রকৃত সত্যে উপনীত হওয়া সম্ভবপর হতো।
এ শ্রেণীর লোকদের কাছে যদি জিজ্ঞেস করা হয় যে, বাদ্যযন্ত্র, সঙ্গীত, দাবা খেলা, নারী শিক্ষা, মেয়েদের মুখমণ্ডল বাহুদ্বয় অনাবৃত রাখা প্রভৃতি সম্পর্কে আপনাদের মত কি? তাহলে তাঁরা বলে বা লিখে দেবেন ‘হারাম’। এক্ষেত্রে পূর্বকালীন মনীষীবৃন্দ কি ভূমিকা গ্রহণ করতেন বা কথা বলার কি ধরণ বা ভঙ্গি অনুসরণ করতেন, তাও তাঁরা ভুলে গেছেন। কেননা যে জিনিস বা কাজ সম্পর্কে চূড়ান্ত ও নিঃসন্দেহভাবে জানা যায়নি যে, তা হারাম, তাঁরা কখনই তাকে হারাম বলতেন না। বরং তাঁরা বলতেন, আমি এটা পছন্দ করি না বা আমি এটা ঘৃণা করি ইত্যাদি। এ প্রেক্ষিতে আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে, এ দুই শ্রেণীর কোন বিশেষ একটি শ্রেণীর মধ্যে নিজেকে শামিল করব না। কেননা আমার দ্বীনই আমাকে পাশ্চাত্যের বান্দা- অন্ধ অনুসরণকারী হতে দেয় না। কেননা আমি তো মহান আল্লাহ্কেই আমার রব্বরূপে স্বীকার করেছি, ইসলামকে আমার জীবনের পূর্ণাঙ্গ বিধানরূপে মেনে নিয়েছি এবং বিশ্বাস করেছি মুহাম্মাদ সা.- ই আল্লাহর শেষ রাসূল।
দ্বিতীয়ত, আমার বিবেক-বুদ্ধি যেহেতু এখনও জাগ্রত, সচেতন, এ কারণে কোন একটি ফকীহ্ মাযহাবকেই আমি সকল বিষয়ের চূড়ান্ত বলে স্বীকার করে নিতে পারি না। কেননা তা যেমন নির্ভুল হতে পারে, তেমনি তো ভুল হওয়ার আশংকা থেকেও সম্পূর্ণ মুক্ত নয়। ইমাম ইবনুল জাওজী বলেছেন, অন্ধ অনুসরণকারী এক অনির্ভরযোগ্য ভিত্তির ওপর নির্ভরশীল হয়ে থাকে। আর তাতে বিবেক-বুদ্ধিকে সম্পূর্ণ অকেজো করে রাখা হয়। বিবেক-বুদ্ধি ও চিন্তা-বিবেচনা শক্তি মানুষের জন্যে আল্লাহ প্রদত্ত একটি মহৎ গুণ। তাকলীদ বা অন্ধ অনুসরণের নীতি গ্রহণ করা হলে এ মহৎ গুণের যাবতীয় কল্যাণ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করা হয়। যার হাতে আলোর মশাল রয়েছে সে যদি তা নিভিয়ে অন্ধকারে পথ চলতে শুরু করে, তবে তার এ হাস্যকর আচরণ কোনক্রমেই যুক্তিসঙ্গত বিবেচিত হতে পারে না।
এ কারণে আমি নিজেকে বিশেষ কোন মাযহাবী গোষ্ঠীর সাথে জড়িত করিনি। কেননা আমার মতে প্রকৃত সত্য বিশেষ একটি মাযহাবী মতের মধ্যে সীমিত হয়ে থাকে নি। দুনিয়ার প্রচলিত এসব মাযহাবের ইমামগণ নিজেদের নির্ভুল নিষ্পাপ হওয়ার দাবিও করেননি কখনও। আসলে তাঁরা ছিলেন সত্যানুসন্ধানের জন্যে প্রাণপণ চেষ্টাকারী মুজতাহিদ। আর কোন ভুল করে থাকলেও তারা এক গুণ সওয়াব পাবেন, আর যদি নির্ভুল ইজতিহাদী মত প্রকাশে সক্ষম হয়ে থাকেন, তাহলে তাঁরা দ্বিগুণ সওয়াব পাবেন। বস্তুতঃ ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানে নিষ্ঠাপূর্ণ ও অনাসক্ত সত্যানুসন্ধানের এটাই হচ্ছে ঘোষিত মর্যাদা।
ইমাম মালিক র. বলেছেনঃ
............ (আরবী)..............
নবী করীম সা. ব্যতীত অন্যান্য সব মানুষেল মর্যাদাই হচ্ছে এই যে, তার কথার কিছু অংশ গ্রহণও করা যায়, বর্জনও করা যায়।
ইমাম শাফেয়ী র. বলেছেনঃ
............ (আরবী)..............
আমার মত নির্ভুল, তবে ভুল হওয়ার আশংকা আছে। আর আমার ছাড়া অন্যান্যদের মত ভুল, তবে নির্ভুল হওয়ার সম্ভাবনা আছে।
সে সুবিজ্ঞ মুসলিম জ্ঞানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন মতের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা-পর্যালোচনা করার এবং তন্মধ্য থেকে কোন একটি মতকে অগ্রাধিকার দেয়ার যোগ্যতা ও উপকরণের অধিকারী, তার পক্ষে মাযহাব সমূহের মধ্য থেকে বিশেষ কোন একটি মাযহাবের নিকট বন্দী হয়ে থাকা কিংবা বিশেষ কোন ফিকাহ্ বিশারদের মতের অন্ধ অনুসারী হওয়া কোনক্রমেই বাঞ্ছনীয় হতে পারে না। বরং তার তো দলিল-প্রমাণের ভিত্তিতে চলার নীতি অবলম্বন করা কর্তব্য। তখন যে দলিলটি নির্ভুল হবে, যার প্রমাণ অকাট্য হবে, সেটিকেই অনুসরণ করে চলবে। আর যার সনদ দুর্বল, দলিলের অকাট্যতা অপ্রমাণিত তা সহজেই পরিত্যক্ত হবে। অতএব এরূপ একটি মত গৃহীত হয়ে থাকলে তাও অবশ্যই পরিত্যক্ত হওয়া উচিত। হযরত আলী রা. নীতিকথা হিসেবে বলেছিলেনঃ
............ (আরবী)..............
লোকদের দেখে সত্যকে চিনবার ও জানবার চেষ্টা কর না। বরং সত্যকে সত্য হিসেবেই জানতে ও চিনতে চেষ্টা কর এবং তারই ভিত্তিতে খোঁজ কর সেই সত্যের ধারক লোকদের।
জামে আযহারের সংস্কৃতি পরিষদের নির্দেশ পালন করতে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা চালিয়েছি। প্রতিটি বিষয়কেই আমি দলিলের ভিত্তিতে পরীক্ষা করতে এবং তুলনা করে মৌল কারণের দৃষ্টিতে কোন একটি মতকে অগ্রাধিকার দিতে চেষ্টা করেছি। এ পর্যায়ে আমি আধুনিক যুগের চিন্তা-ভাবনা ও জ্ঞান-তথ্যকে পুরোপুরি কাজে লাগিয়েছি। সর্বক্ষেত্রেই আমি ইসলামের দৃষ্টিকোণকে স্বর্ণোজ্জ্বল ও অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ ভিত্তিকই পেয়েছি। আর এটাই স্বাভাবিক। কেননা ইসলাম তো বিশ্বমানবতার দ্বীন। আল্লাহ নিজেই বলেছেনঃ
............ (আরবী)..............
আল্লাহর রঙ। আর আল্লাহর রঙের তুলনায় অধিক উত্তম রঙ আর কি হতে পারে?
হালাল-হারামের ব্যাপারটি একটি চিরন্তন ব্যাপার। প্রাচীনকাল থেকেই প্রতিটি জাতির জীবনে এ প্রশ্ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দিয়েছে। তবে হারামের পরিমাণ ও তার প্রকৃতি পর্যায়ে যে মতভেদ রয়েছে তা অস্বীকার করা যায় না। অবশ্য তার কারণও ভিন্ন রয়েছে। এ পর্যায়ের দৃষ্টিকোণ প্রতিটি জাতির প্রাথমিক পর্যায়ের আকীদা-বিশ্বাস ও আবহমানকালের সংস্কার ঐতিহ্যের সাথে গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট।
উত্তরকালে বড় বড় আসমানী দ্বীন শরীয়াতের বিধানসমূহ উপস্থাপিত করেছে। আর তাতে হালাল-হারামের ব্যাপারটি অবশ্যই উপস্থিত রয়েছে। দ্বীনের প্রতি ঈমান গ্রহণের পর ব্যাপারটি নিছক সংস্কার বা গোষ্ঠগত প্রচলন কিংবা রেওয়াজের ব্যাপার হয়ে থাকে নি। তখন তা মানবীয় আদর্শের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। কিন্তু তখন হালাল-হারাম নির্ধারণের অনেক ক্ষেত্রেই সমসাময়িক সমাজ দৃষ্টি ও প্রবণতার প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছে। অবস্থার পরিবর্তনে হালাল-হারামেরও পরিবর্তন ঘটেছে। সময়ের পরিবর্তনের প্রভাবকেও অস্বীকার করা যায় নি। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, ইয়াহূদীদের সমাজে অনেক হারামই ছিল সাময়িক। সে হারাম-সীমালংঘন করার অপরাধে আল্লাহ তা’আলা বনী ইসরাঈলকে শাস্তি দিয়েছেন। যদিও এ হারাম কোন চিরন্তন ব্যাপার ছিল না। হযরত ঈসা আ. বনী ইসরাঈলদের লক্ষ্য করে যে কথা বলেছিলেন, কুরআনে তা উদ্ধৃত হয়েছে এ ভাষায়ঃ
............ (আরবী)..............
আমার পূর্ববর্তী তওরাতের সত্যতা ঘোষণাকারী এবং আমি তোমাদের জন্যে হালাল করে দেব এমন কিছু কিছু জিনিস, যা তোমাদের প্রতি হারাম করে দেয়া হয়েছিল।
পরে দ্বীন-ইসলাম যখন অবতীর্ণ হল, তখন মানবতা পূর্ণতা লাভ করেছে, তা নবুয়্যাত ও রিসালাতের সর্বশেষ অবদান গ্রহণের জন্যে উপযুক্ত হয়ে উঠেছিল। তখন আল্লাহ তা’আলা ইসলামের সর্বশেষ শরীয়াতের শাশ্বত ও চিরস্থায়ী বিধান নাযিল করলেন। সূরা আল-মায়িদার আয়াতে বিভিন্ন হারাম খাদ্যের উল্লেখ করার পর আল্লাহ তা’আলা একথাই ঘোষণা করেছেন নিম্নোদ্ধৃত ভাষায়ঃ
............ (আরবী)..............
আজ তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামত দান সম্পূর্ণ ও সমাপ্ত করলাম এবং তোমাদের জন্যে ইসলামকে দ্বীন হিসেবে মনোনীত করে দিলাম।
বস্তুত ইসলামে হালাল-হারামের চিন্তা অত্যন্ত সহজ-সরল ও সুস্পষ্ট। নভোমন্ডল ও পৃথিবী আল্লাহ্র কাছ থেকে যে আমানতের বোঝা বহনে অক্ষমতা ও অস্বীকৃতি জানিয়েছিল, এ ব্যাপারটি সে আমানতেরও অংশ। কেননা তা মানুষ নিজের স্কন্ধে সাগ্রহে গ্রহণ করেছিল। আর তা হচ্ছে আল্লাহ প্রদত্ত আইন-বিধান পালন ও পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব বহনের আমানত। এ এক কঠিন ও দুর্বহ দায়িত্ব। এ দায়িত্ব গ্রহণের ভিত্তিতেই মানুষকে সওয়াব কিংবা আযাদ দেয়া হবে কিয়ামতের দিন। মানুষ যাতে এ আমানতের বোঝা যথাযথভাবে বহন করতে পারে এবং এতদসংক্রান্ত দায়িত্ব পালনের সমর্থ হয় সেজন্যেই আল্লাহ তা’আলা মানুষকে বিবেক-বুদ্ধি ও ইচ্ছাশক্তি দান করেছেন, নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন এবং জীবন বিধানরূপে নাযিল করেছেন তাঁর মহান গ্রন্থাবলী। এমতাবস্থায় মানুষের এরূপ প্রশ্ন করার অধিকার নেই যে, তাদের জন্যে হালাল-হারাম বিধান কেন দেয়া হল, কেন তাদের উন্মুক্ত ও বল্গাহারা করে ছেড়ে দেয়া হয় না? বস্তুত এ হচ্ছে আল্লাহ্র পরীক্ষণ ব্যবস্থার পরিশিষ্ট। এটা কেবল মানুষের ওপরই প্রবর্তিত। আল্লাহর অসংখ্য সৃষ্টিকুলের মধ্য থেকে কেবলমাত্র মানব জাতিকেই এজন্যে বাছাই করে মনোনীত করা হয়েছে। কেননা মানুষ ফেরেশতাদের ন্যয় নিছক ‘আত্মা’ নয়, নিছক লালসা-কামনা সর্বস্বও নয় জন্তু-জানোয়ারের মতো। মানুষ এ দুটির সমন্বয়- অতীব ভারসাম্যপূর্ণ সৃষ্টি। মানুষ তার এ সমন্বিত সত্তা উন্নীত করে ফেরেশতাদের মর্যাদায় পৌঁছতে পারে, হতে পারে তার চাইতেও উত্তম ও উন্নত। সে সঙ্গে অধঃপতনের নিম্নতম পংকে ডুবে গিয়ে জন্তু-জানোয়ার কিংবা তার চাইতেও নীচে ও নিকৃষ্ট অবস্থায় উপনীত হতে পারে।
অপর এক দৃষ্টিতে এ হালাল-হারামের ব্যাপারটি ইসলামী শরীয়াত বিধানের আকাশে সদা আবর্তনশীল। মানুষের কল্যাণ বিধান এবং ক্ষতি ও দুর্ভাগ্য মোচনের ভিত্তির ওপর তা প্রতিষ্ঠিত। এর দ্বারা মানুষের জীবনকে সুষ্ঠু, সুন্দর ও সহজতর করাই উদ্দেশ্য। এ বিধান যেমন একদিকে সমস্ত বিপর্যয় প্রতিরোধ করে, তেমনি সমস্ত কল্যাণকে সক্রিয় করে তোলে। সমগ্র মানবতার সার্বিক কল্যাণ বিধানই তার চরম লক্ষ্য। তার আত্মার কল্যাণ, দেহের কল্যাণ, বিবেক-বুদ্ধির সুস্থতা এ বিধান পালনেই নিহিত। মানুষ বিভিন্ন জাতি, বর্ণ, দেশ-কাল প্রভৃতিতে বিভক্ত হওয়া সত্ত্বেও এ বিধান থেকেই কল্যাণ লাভ করতে সক্ষম।
এ বিধান দ্বীন-ইসলামের অবিচ্ছিন্ন অংশ। এ দ্বীন নাযিল হয়েছে সমগ্র মানুষের জন্যে সার্বিক কল্যাণের ও রহমতের বাহন হিসেবে। এ কথা আল্লাহ তা’আলা বলেছেন তাঁর সর্বশেষ রাসূলকে সম্বোধন করেঃ
............ (আরবী)..............
সমগ্র বিশ্বজগতের প্রতি রহমতরূপেই তোমাকে পাঠিয়েছি।
রাসূল সা. নিজেও বলেছেনঃ
............ (আরবী)..............
নিঃসন্দেহে আমি সুপরিশীলিত রহমত মাত্র।
এ রহমতের ফল হিসেবেই আল্লাহ তাঁর এ সর্বশেষ উম্মতের উপর থেকে সর্বপ্রকার কষ্ট, কঠোরতা ও কৃচ্ছ সাধনার নিয়মাদি তুলে নিয়েছেন। ‘সব কিছু বৈধ- কোন কিছুই নিষিদ্ধ হয়’, এ নীতির কদর্যতা থেকেও তাদের মুক্ত করেছেন। মূর্তিপূজারী ও কোন কোন কিতাবী ধর্ম-পালনকারী গোষ্ঠী আবার কৃচ্ছ সাধনা ও কষ্ট-কঠোরতার নীতি অনুসরণ করতে গিয়ে সকল প্রকার পাক-পবিত্র জিনিসকে নিজেদের জন্যে হারাম করে নিয়েছে এবং বহু প্রকার জঘন্য ঘৃণ্য কাজ বা জিনিসকে নিজেদের জন্যে ‘হালাল’ করে নিয়েছে। আল্লাহ নিজেই বলেছেনঃ
............ (আরবী)..............
আমার রহমত প্রতিটি জিনিসকেই আচ্ছন্ন করে রেখেছে। আমি অবশ্য তা নির্দিষ্ট করে দেব সেসব লোকদের জন্যে, যারা আল্লাহ্কে ভয় করে, যাকাত দেয় এবং যারা আমাদের আয়াতসমূহের প্রতি ঈমানদার তারাই উম্মী নবীকে অনুসরণ করে চলে। তাদের কাছে রক্ষিত তওরাত ও ইঞ্জিলে তাঁর কথা লিখিত দেখতে পায়। এ নবীই তাদের ভাল ভাল কাজের আদেশ করে, অন্যায় ও পাপ কাজ থেকে বিরত থাকতে বলে, তাদের জন্যে ভাল ভাল ও পবিত্র জিনিসসমূহ হালাল ঘোষণা করে, তাদের জন্যে হারাম ঘোষণা করে সব নিকৃষ্ট ও জঘন্য বীভৎস কাজ বা দ্রব্যসমূহ এবং তাদের ওপর যে বোঝা ও শৃঙ্খল আবহমানকাল থেকে চেপে বসে আছে, তা থেকে তাদের মুক্ত করে।
হালাল-হারামের ব্যাপারে ইসলামী বিধান যে দুটি আয়াতের ওপর ভিত্তিশীল, তার উল্লেখ এ গ্রন্থের শুরুতে দেয়া হয়েছে।
শেষ কথা হচ্ছে, হালাল-হারাম বিষয়ে লিখিত এ ক্ষুদ্র পরিসর গ্রন্থখানির গুরুত্ব স্বীকৃত হতে হবে বলে আমি বিশ্বাস করি। আধুনিক মুসলিম গ্রন্থ প্রণয়ন পর্যায়ে এটি একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন বলে মনে করি। এ গ্রন্থ মুসলিম জীবনের বহু সমস্যার সমাধান করবে এবং বহু ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত বিষয়াদি সংক্রান্ত প্রশ্নের সঠিক জবাব জনসমক্ষে উপস্থাপিত করবে। মুসলিমদের জন্যে হালাল কি, হারাম কি এবং তার নিহিত প্রকৃত কারণ ও যুক্তি কি, তা সব বিস্তারিতভাবে এ গ্রন্থের মাধমে জানা যাবে বলে আমার দৃঢ় প্রত্যয় রয়েছে।
সর্বশেষে জামে আযহারের ভাইস চ্যান্সেলর ও ইসলামী সংস্কৃতি পরিষদের প্রতি শুকরিয়া না জানালে আমার দায়িত্ব পালন হবে না। কেননা তাঁদের কথানুযায়ীই আমি এ গ্রন্থ পণয়নে উদ্যোগী হয়েছি।
ইসলামে হালাল-হারামের বিধান
প্রথম অধ্যায়
- সংজ্ঞা
- সমস্ত জিনিস মূলত মুবাহ- জায়েয
- হালাল বা হারাম নির্ধারণ কেবলমাত্র আল্লাহ্র অধিকার
- হালালকে হারাম করা এবং হারামকে হালাল ঘোষণা করা শিরক
- হারাম জিনিসমূহে অত্যন্ত ক্ষতিকর
- হালাল জিনিস মানুষকে হারাম নির্ভর হওয়া থেকে মুক্ত করে
- যা হারামের কারণ তাও হারাম
- হারামের ব্যাপারে কৌশল অবলম্বনও হারাম
- নিয়ত ভাল হলেই হারাম জিনিস হালাল হয়ে যায় না।
- হারাম জিনিস থেকে নিজকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে সন্দেহের জিনিসমূহ পরিহার করে চলা
- হারাম সকলের জন্যেই হারাম
- প্রয়োজন তীব্র হলে অনেক নিষিদ্ধ জিনিসও মুবাহ হতে পারে
সংজ্ঞা
হালালঃ মুবাহ, নিষিদ্ধ নয় এমন শরীয়াত প্রবর্তক যা করার অনুমতি দিয়েছেন কিংবা যা করতে নিষেধ করেন নি।
হারামঃ শরীয়াতদাতা যা স্পষ্ট ভাষায় নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন, যা করলে পরকালে অবশ্যই জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হতে হবে। অনেক সময় দুনিয়ায়ও দণ্ড ভোগ করতে হবে।
মাকরূহঃ যে কাজ করতে শরীয়াতদাতা নিষেধ করেছেন, কিন্তু খুব কড়াকড়িভাবে নিষেধ করেন নি। হারামের তুলনায় এর নিষিদ্ধতা অনেক কম ও ক্ষীণ। হারাম কাজ করলে যে শান্তি প্রাপ্য, মাকরূহ করলে তা পেতে হয় না। তবে ক্রমাগতভাবে মাকরূহ কাজ করতে থাকলে হারাম কাজের শাস্তি ভোগ করতে হবে।
ইসলাম-পূর্ব লোকেরা বহু দিক দিয়েই চরম গুমরাহীর মধ্যে নিমজ্জিত ছিল। হালাল-হারামের ব্যাপারটি ছিল তন্মধ্যে অন্যতম। এ পর্যায়ে তাদের গুমরাহীর রূপ ছিল এই যে, তারা হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল মনে করে নিয়েছিল। এ ব্যাপারে সাধারণ মুশরিক এবং আহলে কিতাব ইয়াহূদী ও খ্রীস্টান সকলেরই দৃষ্টিকোণ ছিল সম্পূর্ণ অভিন্ন। এ গুমরাহী দুটি চরম প্রান্তিকে উপনীত হয়েছিল। ভারতীয় ব্রাহ্মণ্যবাদ ও খ্রীস্টীয় বৈরাগ্যবাদ পৌঁছে গিয়েছিল চরমে। যেসব ধর্মমতে দেহকে কষ্ট ও পীড়ন দান বৈধ ছিল, উত্তম খাদ্য-বস্ত্র ও অলংকার-চাকচিক্যমণ্ডিত জিনিসপত্র ব্যবহার করাকে হারাম ঘোষণা করেছিল, তাও ছিল সেই চরমেই উপনীত। কোন কোন বৈষ্ণব-বৈরাগীর মতো পা ধোয়া এবং গোসল করাও গুনাহের কাজরূপে নির্দিষ্ট হয়েছিল।
পারস্যে মুজ্দাক ধর্মমত ছিল অপর এক প্রান্তিক সীমায় অবস্থিত। এ মতে সব কিছুই ছিল ‘মুবাহ’- বৈধ- বলে বিবেচিত। কোন কিছুই নিষিদ্ধ ছিল না। মানুষের ইয্যত-আবরূ মানুষের কাছে অতীব পবিত্র ও সম্মানার্হ বিষয় হলেও তা ক্ষুণ্ন বা নষ্ট করা এ ধর্মমতের দৃষ্টিতে কিছুমাত্র অন্যায় ছিল না।
জাহিলিয়াতের যুগে আরবরা হালাল-হারামের একটা সম্পূর্ণ ভুল মানদণ্ড ঠিক করে নিয়েছিল। তাদের মত মদ্যপান, বেশি বেশি সুদ খাওয়া, নারীদের সাথে অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন কিংবা তাদের সাথে নির্যাতনমূলক আচরণ ও সন্তান হত্যা প্রভৃতি ধরণের জঘন্যতম কাজেও কিছুমাত্র দোষ বা আপত্তি ছিল না। সন্তান হত্যার ন্যায় জঘন্য ও বীভৎস কাজকে লোভনীয় আকর্ষনীয় ও গৌরবজনক কাজরূপে চিত্রিত করা হয়েছিল। এজন্যে পিতৃ হৃদয়ে একবিন্দু মমতাও থাকত না এবং এ জঘন্য কাজ থেকে তাদের বিরত রাখতে পারত না। এ পর্যায়েই কুরআন মজীদে বলা হয়েছেঃ
وَكَذَٰلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ
এবং এমনিভাবে তাদের শরীকরা বহু সংখ্যক মুশরিকদের জন্যে তাদের নিজেদের সন্তানকে হত্যা করার কাজকে খুবই আকর্ষণীয় বানিয়ে দিয়েছে যেন তারা তাদেরকে ধ্বংসের মধ্যে নিমজ্জিত করে, এবং তাদের নিকট তাদের দ্বীনকে সন্দেহপূর্ণ বানিয়ে দেয়। (সূরা আন’আমঃ ১৩৭)
এ উদ্দেশ্যে তখন কতিপয় কথা রচনা করে তার বৈধতা প্রমাণ করতে চেষ্টা করা হয়েছে। আর সে কথাগুলো হচ্ছে, অভাব-অনটন ও দারিদ্রের আশংকা, কন্যা সন্তান হওয়াটা লজ্জার কারণ প্রভৃতি। নিজেদের উপাস্যদের নৈকট্য লাভ করার উদ্দেশ্যে সন্তানদের বলিদান করতেও তারা কুণ্ঠিত হতো না। বড়ই আশ্চর্যের বিষয়, একদিকে তারা কলিজার টুকরা সন্তান হত্যা করা কিংবা জীবন্ত প্রোথিত করাকে সম্পূর্ণ বৈধ মনে করে নিয়েছিল। অপরদিকে তারা বহু প্রকারের পবিত্র ও হালাল ফসল এবং জন্তু ভক্ষণকে নিজেদের জন্যে হারাম করে নিয়েছিল। আর চরম মাত্রার বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, এ নিষেধের কথাকে তারা দ্বীনের বিধান বলে প্রচার করে বেড়াত। তাদের দাবি ছিল, স্বয়ং আল্লাহ্ই এ সব জিনিস হারাম করে দিয়েছেন।
কিন্তু এ কথা ছিল সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। আল্লাহ্ তা’আলা তাদের এ দাবির প্রতিবাদ করে ইরশাদ করেছেনঃ
وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَّا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَّا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ ۚ سَيَجْزِيهِم بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ
আর তারা বলত এসবই চতুষ্পদ জন্তু ও ক্ষেত্রের ফসল হারাম। তা খেতে পারবে না কেউ- তবে আমরা যাদের চাব তারা খাবে। এটা তাদের মনগড়া ধারণা। আরও কতিপয় জন্তু রয়েছে, যাদের পৃষ্ঠকে হারাম করা হয়েছে, এছাড়া যেসব জন্তুর ওপর যবাই করা কালে আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করে না আল্লাহর ওপর মিথ্যা আরোপ করতে গিয়ে, তাদের এ মিথ্যা আরোপের প্রতিফল তাদের অবশ্যই দেয়া হবে। (সূরা আন’আমঃ ১৩৮)
যেসব জিনিস হারাম হওয়া উচিত, তাকে যারা হালাল করে নিয়েছে এবং যা হালাল হওয়া বাঞ্ছনীয়, তাকে যারা হারাম করে নিয়েছে, তারা যে সত্য পথ থেকে বিভ্রান্ত হয়ে গেছে, কুরআন মজীদ তা সুস্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছে। কুরআন বলছেঃ
........... (আরবী) ..........
যেসব লোক নির্বুদ্ধিতার কারণে কোনরূপ জ্ঞান ও যুক্তি ব্যতীত নিজেদের সন্তান হত্যা করছে িএবং আল্লাহর দেয়া রিযিককে হারাম গণ্য করেছে- আল্লাহ সম্পর্কে ভিত্তিহীন মনোভাব পোষণ করে, তারা ভয়ানক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এরা সকলেই গুমরাহ হয়ে গেছে এবং কখনও হেদায়েতপ্রাপ্ত হবে না।
ইসলাম যে অবস্থার মধ্যে নাযিল হয়েছিল, তখন তা হালাল-হারাম নির্ধারণে এরূপ বিকৃতি ও গুমরাহীরই সম্মুখীন হয়েছিল। এমন কিছু ভিত্তি রচনা করতে হয়েছিল, যার ওপর ভিত্তি করে এ হালাল-হারামের ব্যাপারটি চূড়ান্ত মীমাংসা হতে পারে। তার জন্যে একটা মানদণ্ড নির্ধারণ করতে হয়েছে। তার ওপর রেখে প্রতিটি ব্যাপারকে সুষ্ঠুভাবে যাচাই করা হয়েছে। এ জন্যে সুবিচারের মাপকাঠি সর্বসমক্ষে দাঁড় করাতে হয়েছে এবং তার ভিত্তিতে অতীব ভারসাম্যপূর্ণভাবে হালাল-হারাম নির্ধারণ করা হয়েছে। এর ফলেই মুসলিম উম্মতকে ‘মধ্যম নীতি অবলম্বনকারী জাতি’- (আরবী) বলে ঘোষণা করা শোভনীয় হয়েছিল। কেননা একদিকে রয়েছে গুমরাহ্-পথভ্রষ্ট জাতি; অপরদিকে বিকৃতকারী জাতি- ডানে ও বামে। আর তার মাঝখানে মুসলিম জাতির অবস্থিতি। তারা উভয় দিকের দোষমুক্ত। এ জন্যেই আল্লাহ তাদের ‘উত্তম জাতি’ নামেও অভিহিত করেছেন। বলেছেন, বিশ্বমানবতার কল্যাণের উদ্দেশ্যেই এ জাতির সৃষ্টি।
১. সব জিনিসের ব্যাপারেই মৌল নীতি হচ্ছে- তা মুবাহ
শরীয়াতের বিধান প্রণয়নে ইসলামের সর্বপ্রথম মৌল নীতি হচ্ছে আল্লাহ্ তা’আলা মানুষের জন্যে যত জিনিসই সৃষ্টি করেছেন, তা সবই হালাল ও মুবাহ্। শরীয়াতের বিধান রচয়িতার অকাট্য, সুস্পষ্ট ও প্রমাণিত ঘোষণায় যদি কোনটিকে ‘হারাম’ বলে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে তবে কেবল সেটিই হারাম। কিন্তু কোন বিষয়ে যদি অকাট্য কোন ঘোষণা প্রমাণিত না হয় কিংবা কোন দলিল থেকে যদি অকাট্য কোন ঘোষণা প্রমাণিত না হয় কিংবা কোন দলিল থেকে যদি সুস্পষ্টভাবে কোন জিনিসের হারাম হওয়ার কথা নিঃসন্দেহে জানা না যায়, তাহলে তার তার মৌল অবস্থা- মুবাহ্ হওয়ার অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকবে। তাকে হারাম বলা যাবে না। কোন যয়ীফ হাদীস এক্ষেত্রে দলিল হিসেবে গ্রহণীয় হতে পারে না।
আল্লাহ্ সৃষ্ট সব জিনিসই যে মূলগতভাবে হালাল তা কোন মনগড়া কথা নয়। তা কুরআন মজীদের বহু কয়টি আয়াতে সুস্পষ্ট ঘোষণা থেকে অকাট্যভাবে প্রমাণিত। এ পর্যায়ের কয়েকটি আয়াত এখানে উদ্ধৃত করা যাচ্ছেঃ
هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا
সেই মহান আল্লাহ্ই তোমাদের (ভোগ-ব্যবহারের) জন্যে সৃষ্টি করেছেন সে সব কিছুই যা আছে এ পৃথিবীতে। (সূরা বাকারাঃ ২৯)
وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ
নভোমণ্ডল ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, তার সব কিছুই আল্লাহ্ তোমাদের জন্যে কর্মে নিরত করে রেখেছেন। (সূরা জাছিয়াহঃ ১৩)
أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً
তুমি কি লক্ষ্য করনি, নভোমণ্ডলে ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা সবই আল্লাহ্ তা’আলা মানুষের কল্যাণের জন্যে নিয়োজিত করে রেখেছেন এবং তোমাদের প্রতি বাহ্যিক ও গোপনীয়- দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান নিয়ামতসমূহ উদারভাবে ঢেলে দিয়েছেন? (সূরা লোকমানঃ ২০)
এ সব ঘোষণা থেকে সুস্পষ্ট ও অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়, আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীস্থ সব কিছুই আল্লাহ্ তা’আলা মানুষের জন্য- মানুষের কল্যাণের ও রোগ-ব্যবহারের জন্যেই সৃষ্টি করেছেন, কর্মে নিবদ্ধ করে রেখেছেন। এ কথা বলে আল্লাহ্ মানুষের প্রতি তাঁর অপরিসীম অনুগ্রহের কথাই জানিয়ে দিয়েছেন। তাহলে বিশ্বলোকের সব কিছুই মানুষের জন্যে অবশ্যই হালাল হবে। তার কোন একটির ভোগ-ব্যবহার মানুষের নিষিদ্ধ হতে পারে না, সব কিছুর পক্ষেই আল্লাহ্র অনুমতি নিরাজিত। এ সবই তো আল্লাহর দেয়া নিয়ামত। তা যদি নিষিদ্ধই হবে, তাহলে তা সব মানুষের জন্যে সৃষ্টি করার কথা বলার কি তাৎপর্য থাকতে পারে?
তবে আল্লাহ নিজেই যদি সৃষ্ট সব কিছুর মধ্য থেকে কিছু কিছু জিনিস হারাম করে দিয়ে থাকেন, তাহলে সে কথা স্বতন্ত্র। এরূপ কোন কোন জিনিস বিশেস কারণে ও বিশেষ কল্যাণ-উদ্দেশ্যে হারাম করে দিয়ে থাকলে তা অবশ্যই মানতে হবে। তা সাধারণভাবে হালাল কর দেয়ার ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম মাত্র এবং সে ব্যতিক্রমের মূলে নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে বলে মনে করতে হবে।
এ প্রেক্ষিতে বলা যায়, ইসলামী শরীয়াতে হারামের পরিধি খুব বেশি সংকীর্ণ। হালালের ক্ষেত্র বিপুলভাবে বিস্তীর্ণ ও প্রশস্ত। কেননা সুস্পষ্ট অকাট্য ভাষায় হারাম ঘোষণাকারী আয়াত খুবই অল্প এবং তা কয়েকটি মাত্র। ইতিবাচকভাবে যে সব বিষয়ে নতুন করে কিছু বলা হয়নি- না হালাল, না হারাম, তা তো সে মৌল নীতির ভিত্তিতেই বিবেচিত হবে। আল্লাহ্র ক্ষমার সীমার মধ্যে গণ্য হবে।
এই পর্যায়ে রাসূলে কারীম সা.- এর ঘোষণাও উল্লেখ্য। তিনি ইরশাদ করেছেনঃ
......... (আরবী)..........
আল্লাহ তাঁর কিতাবে যা হালাল করেছেন তা হালাল, যা হারাম করেছেন তা হারাম। আর যে বিষয়ে তিনি নীরবতা অবলম্বন করেছেন, তাতে ক্ষমা রয়েছে। অতএব তোমরা আল্লাহ্র কাছ থেকে তাঁর ক্ষমা গ্রহণ কর। কেননা আল্লাহ্ তো কোন কিছু ভুলে যান না- (ভুলবশত বলেন নি এমন তো হতে পারে না)। এ কথার প্রমাণ হিসেবে তিনি পাঠ করলেনঃ ‘‘তোমাদের প্রভু ভুলে যান না।’’ (কুরআনের একটি আয়াতের অংশ)
হযরত সালমান ফারসী বর্ণনা করেছেনঃ
.............. (আরবী).............
রাসূলে কারীম সা. কে চর্বি, মাখন, পনির ও কোমল পশু লোমের তৈরী বস্ত্রাদি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেনঃ আল্লাহ্ তাঁর কিতাবে যা হালাল ঘোষণা করেছেন, তা হালাল। যা হারাম ঘোষণা করেছেন তাঁর কিতাবে, তা হারাম। আর যে বিষয়ে তিনি নীরবতা অবলম্বন করেছেন, তা সেসব জিনিসের মধ্যে গণ্য যা করলে আল্লাহ্ ক্ষমা করে দেবেন।
প্রশ্নের উত্তরে রাসূলে করীম সা. এক-একটি জিনিস সম্পর্কে কোন কথা বলেন নি। এ পর্যায়ে শাশ্বত নীতিই তিনি ঘোষণা করলেন, যে নীতির ভিত্তিতে হালাল-হারাম নির্ধারিত হয়ে থাকে এবং হওয়া উচিত। আল্লাহ কোন্ কোন্ জিনিস হারাম করেছেন, তা এ মূলনীতির ভিত্তিতে অতি সহজেই নির্ধারিত হতে পারে। আর অতঃপর যে সব বিষয়ে হারামের কোন ঘোষণা পাওয়া যাবে না, তা সবই হালাল বলে বিবেচিত হবে।
নবী কারীম সা. বলেছেনঃ
............ আরবী .............
আল্লাহ তা’আলা কতগুলো কাজকে ফরয করে দিয়েছেন। অতএব তোমরা তা নষ্ট করে ফেল না। তিনি কতগুলো সীমা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, তোমরা সে সীমা লংঘন করো না। কিছু কিছু জিনিসকে তিনি হারাম করেছেন, তোমরা তার বিরোধিতা করো না। আর তোমাদের প্রতি অনুগ্রহবশত- না ভুলে গিয়ে অনেক বিষয়ে তিনি পূর্ণ নীরবতা অবলম্বন করেছেন। অতএব সে বিষয়ে তোমরা বিতর্কে লিপ্ত হয়ো না। (তিরমিযী, ইবনে মাযাহ)
এ পর্যায়ে আমি একটি বিষয়ে সতর্কবাণী উচ্চারণ করতে চাই। ‘মৌলিকভাবে সব কিছুই মুবাহ্’ কথাটি কতগুলো দ্রব্য-সামগ্রীর ব্যাপারেই প্রযোজ্য নয়। যাবতীয় কাজকর্ম, হস্তক্ষেপ, পদক্ষেপ গ্রহণ ইত্যাদি- যা ইবাদতের ব্যাপারসমূহে গণ্য নয় সেক্ষেত্রেও এ মৌল নীতিটি প্রযোজ্য। এগুলো আমরা বলি আদত-অভ্যাস, পারস্পরিক কার্যাদি। এসবের মূল কথা হলো, আসলে তা সবই অ-হারাম- শর্তহীনভাবেই তা হালাল। তবে শরীয়াতদাতা যদি কোন কাজকে হারাম ঘোষণা করে থাকেন এবং কোন বিষয়ে কোন শর্ত আরোপ করে থাকেন, তবে তা অবশ্যই হারাম হবে এবং সে শর্তকে অবশ্যই মানতে হবে। এ পর্যায়ে আল্লাহ্র ঘোষণা হচ্ছেঃ
............. আরবী ..............
তোমাদের প্রতি যা যা হারাম করা হয়েছে, তার সব কিছুই সুস্পষ্ট করে তিনি তোমাদের বলে দিয়েছেন।
এ ঘোষণা দ্রব্যাদি ও কার্যাদি উভয় ব্যাপারেই প্রযোজ্য। কিন্তু ইবাদতের ব্যাপার এ থেকে স্বতন্ত্র ও ভিন্নতর। কেননা তা-ই হচ্ছে আসল দ্বীন- দ্বীনের মৌল ব্যাপার আর তা কেবলমাত্র ওহীর সূত্রেই লাভ করা যেতে পারে। ওহীর মাধ্যমে যা ইবাদত বলে জানা যায়নি, তা কখনই এবং কোনক্রমেই ইবাদতের মধ্যে গণ্য হতে পারে না। এ সম্পর্কে রাসূলে কারীম সা.- এর ঘোষণা হচ্ছেঃ
............ আরবী ..............
আমাদের এ দ্বীনের মধ্যে শামিল নয় এমন কোন জিনিস যদি কেউ দ্বীনের মধ্যে নতুন করে উদ্ভাবন করে তবে তা অবশ্যই প্রত্যাখাত হবে। (বুখারী, মুসলিম)
কেননা প্রকৃত দ্বীন দুটো কাজের মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়। একটি হচ্ছে এই যে, বন্দেগী করা হবে কেবলমাত্র এক আল্লাহ্র- এক আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো বন্দেগী করা হবে না। এবং দ্বিতীয়টি এই যে, কেবলমাত্র আল্লাহ্র বন্দেগী করা হবে কেবলমাত্র আল্লাহ্র দেয়া বিধান অনুযায়ী, অন্য কোনভাবে নয়। কাজেই কেউ যদি নিজের পক্ষ থেকে ইবাদতের কোন পন্থা বা অনুষ্ঠান উদ্ভাবন করে- সে যে-ই হোক না কেন- তা গুমরাহী ছাড়া আর কিছুই নয়। তা গ্রহণ করা নয়, প্রত্যাখ্যান করতে হবে ঈমানদার লোকদের। কেননা শরীয়াতের বিধান রচয়িতা তো কেবলমাত্র আল্লাহ্। তিনিই ইবাদত পাওয়ার অধিকারী, ইবাদতের পন্থা ও নিয়ম কেবল তিনিই বলে দিতে পারেন, অন্য কেউ নয়। আর তাঁর প্রদর্শিত পথ-পন্থা ও নিয়মে ইবাদত করা হলেই তা তাঁর কাছে গৃহীত হতে পারে, কেবল সেই ইবাদতের মাধ্যমেই আল্লাহ্র নৈকট্য অর্জিত হতে পারে।
তবে সাধারণ অভ্যাস-আদত কিংবা পারস্পরিক লেনদের সম্পর্ক বিনিময় প্রভৃতি পন্থা ও পদ্ধতির উদ্ভাবক মানুষ নিজে, শরীয়তদাতা নন। শরীয়াতদাতা এ পর্যায়ে শুধু বলে দেবেন কোন্ পন্থা- পদ্ধতি বা নিয়ম ঠিক- যথার্থ এবং কোন্টি যথার্থ নয়। যে ধরণের কাজ বিপর্যয় ও ক্ষতি মুক্ত সেগুলোকে তিনি বহাল রাখারই পক্ষপাতী।
ইমাম ইবনে তাইমিয়া বলেছেনঃ বান্দাদের কথাবার্তা ও কাজকর্ম সংক্রান্ত তৎপরতা দু’ধরণের। কতগুলো আছে ইবাদত, যদ্দারা লোকদের দ্বীনী অবস্থার সংশোধন সাধিত হয়। আর কতগুলো আছে আদত-অভ্যাস, দুনিয়ায় বসবাস করার জন্যে তা মানুষের জীবনে জরুরী। এ পর্যায়ে শরীয়তের দৃষ্টিকোণ হল আল্লাহ যেসব ইবাদত ফরয করে দিয়েছেন কিংবা যা তিনি পছন্দ করেন, তা শরীয়তের বিধঅন ব্যতীত অন্য কোনভাবে প্রমাণিত হতে পারে না।
তবে মানুষের আদত-অভ্যাস সংক্রান্ত ব্যাপারাদির কথা স্বতন্ত্র। কেননা তা তো মানুষ নিজেদের প্রয়োজনে নিজেরাই উদ্ভাবন করে। এসব উদ্ভাবনের পর্যায়ে প্রশ্ন থাকবে শুধু এই যে, তা যেন শরীয়তের পরিপন্থী না হয়। আর আল্লাহ্ স্বয়ং যে বিষয়ে কোন আপত্তি করেন নি, সে বিষয়ে অপর কারো আপত্তির কোন গুরুত্ব থাকতে পারে না। আদেশ-নিষেধ- উভয়টিই শরীয়তের বিধান। ইবাদত হবে শুধু সেসব কাজ, যার নির্দেশ দেননি, সে বিষয়ে নিষেধবাণী উচ্চারণ করার অন্য কার কি অধিকার থাকতে পারে?
এ কারণে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল র. প্রমুখ হাদীস-পারদর্শী ফকীহ্গণ বলতেন যে, ইবাদতসমূহ মূলত ওহী সূত্রে প্রমাণিত। কাজেই শরীয়তের বিধান শুধু তাই, যার পক্ষে শরীয়তের কোন ফয়সালা এসেছে। যে সম্পর্কে তেমন কিছুই নেই, তাকে শরীয়তের অন্তর্ভুক্ত মনে করা আল্লাহ্র ওপর কর্তৃত্ব করার শামিল। এ পর্যায়েই আল্লাহ্র এ আয়াত ঘোষিত হয়েছেঃ
أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ
ওদের জন্যে এমন সব শরীক উপাস্য আছে নাকি, যারা ওদের জন্যে এমন বিধান রচনা করে দিয়েছে, যার কোন অনুমতিই আল্লাহ্ দেন নি? (সূরা শূরাঃ ২১)
এ কারণেই মানুষের সাধারণ আদত-অভ্যাসের ব্যাপারটি ভিন্নতর। আসলে তা সবই মুবাহ- দোষমুক্ত, অনির্দিষ্ট। তার মধ্য থেকে যে যেটিকে আল্লাহ হারাম ঘোষণা করেছেন, কেবল সে সেটিই হারাম হবে, অন্য কিছু নয়। এ কথাকে সত্য না মানলে আমাদের প্রতি এ আয়াতটি প্রযোজ্য হবেঃ
قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا
আল্লাহ্ তোমাদের জন্যে যে রিয্ক নাযিল করেছেন, তন্মধ্য থেকে কিছু তোমরা হারাম বানিয়েছ আর কিছু হালাল? .......এটা কি রকম কাজ তা কি তোমরা ভেবে দেখেছ? (সূরা ইউনুসঃ ৫৯)
এ হচ্ছে অতীব গুরুত্বপূর্ণ ও অধিক কল্যাণবহ মৌল নীতি বিশেষ। এ মৌল নীতির ভিত্তিতে আমরা বলবো, ক্রয়-বিক্রয়, হেবা, ইজারা ইত্যাদি মানুষেল সামাজিক জীবনের আদত-অভ্যাস বা প্রচলনের ব্যাপার। এ দুনিয়ায় জীবন যাপনের জন্যে এগুলো মানুষকে মেনে চলতে হয়- যেমন পানাহার ও পোশাক পরিধান মানুষের অপরিহার্য হয়ে থাকে। এসব ক্ষেত্রে শরীয়ত উত্তম ও সুষ্ঠু নিয়মাদি শিক্ষা দিয়েছে। তাই যে যে ক্ষেত্রে কোনরূপ বিপর্যয় পরিলক্ষিত হয়েছে শরীয়ত তা নিষিদ্ধ করে দিয়েছে এবং যা একান্তই জরুরী তা অপরিহার্য কর্তব্য বলে ঘোষণা করেছে। অতঃপর যা যা অবাঞ্ছনীয় দেখা গেছে, সে সবকে ‘মাকরূহ’ বলেছে আর যে যে কাজে সার্বিক কল্যাণ লক্ষ্য করা গেছে, সেগুলোকে বলেছেন মুস্তাহাব। ফলে এক্ষেত্রের কাজগুলোকে আমূল উৎপাটিত করার বা নতুন করে ঢালাই করার প্রয়োজন হয়নি।
এ সত্য প্রতিভাত হওয়ার পর বলা যায়, লোকেরা নিজেদের ইচ্ছেমত লেন-দেন, ব্যবসায়-বাণিজ্য ও মজুরী বিনিময়ে কাজ করার জন্যে সম্পূর্ণ স্বাধীন, যতক্ষণ না শরীয়ত তার কোন কাজকের হারাম বলে ঘোষণা করছে। লোকদের পানাহারের ব্যাপারটির দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে যা যা হারাম, তা পরিহার করে চললেই হলো। এ ছাড়া এক্ষেত্রে আর কোন বিধি-নিষেধের নিয়ন্ত্রণ মেনে চলতে বাধ্য করা হয়নি। ফলে তা সবেই মৌলিকভাবে মুবাহ-অনিষিদ্ধ।
.............. আরবী .............
এ মৌল নীতির ভিত্তিতে ইবনে তাইমিয়ার ছঅত্র ইমাম ইবনুল কাইয়্যেম এবং হাম্বলী মাযহাবের সব ফিকাহবিদই বলেছেনঃ
.............. আরবী .............
চুক্তি ও শর্তাদি মূলত সবই মুবাহ। যে চুক্তি সম্পর্কে শরীয়ত কোন আপত্তি করেনি এবং যা হারাম ঘোষিত হয় নি, তা সবই হালাল।
সহীহ্ হাদীস থেকেও এ মৌল নীতির সমর্থন পাওয়া যায়। হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ বলেছেনঃ
................ আরবী ................
আমরা আযল করছিলাম, তখন কুরআন নাযিল হচ্ছিল। নিষেধ করার মতো কিছু থাকলে কুরআন তা অবশ্যই নিষেধ করে দিত। [তাই বলে ‘আযল’ নিষিদ্ধ নয়, এমন কথা বলা যাবে না। কেননা এ হাদীসটি প্রাথমিক পর্যায়ের। পরে অন্যান্য হাদীসে তার নিষেধও বর্ণিত হয়েছে। -অনুবাদক]
এ থেকে শুধু এতটুকুই প্রমাণ করতে চাচ্ছি যে, যে বিষয়ে ওহীসূত্রে কোন নিষেধ আসেনি তা অনিষিদ্ধ, তা হারাম নয়। নিষেধকারী কোন ঘোষণা নাযিল না হওয়া পর্যন্ত তা সম্পূর্ণ জায়েয। শরীয়ত সম্পর্কে এ ছিল সাহাবীদের বিশ্বাস এবং তাঁরা যে শরীয়তের মূলতত্ত্ব যথার্থ বুঝতে পেরেছিলেন, তা এ কথা থেকেই অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়।
মোটকথা এ সব দৃষ্টান্ত ও দলিল থেকে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, সে ইবাদত ও সে নিয়মের ইবাদতই শরীয়তসম্মত, যা স্বয়ং আল্লাহ তা’আলা বিধিবদ্ধ করে দিয়েছেন। আর মানুষের আদত-অভ্যাসের মধ্য থেকে হারাম শুধু তা-ই যা স্বয়ং আল্লাহ তা’আলা হারাম ঘোষনা করেছেন। আল্লাহ্ যা হারাম করেন নি, তা কখনই হারাম হতে পারে না।
২. হালাল-হারাম ঘোষণা করার অধিকার একমাত্র আল্লাহ্র
আল্লাহ্র ইসলাম দ্বিতীয় মৌল নীতি হিসেবে ঘোষণা করেছে যে, হালাল-হারাম ঘোষণা করার অধিকার কেবলমাত্র সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা’আলার। সৃষ্টির হাত থেকে এ কর্তৃত্ব কেড়ে নেয়া হয়েছে। আল্লাহ্র দ্বীনের বা বৈষয়িকতার দৃষ্টিতে তার মর্যাদা যা-ই হোক না কেন, এ অধিকার কারোরই নেই। এ কর্তৃত্ব কেবলমাত্র আল্লাহ্র অধিকার বলে স্বীকৃতব্য। আলেম, পীর-দরবেশ, রাজা-বাদশাহ্, নেতা, আল্লাহ্র বান্দাদের ওপর কোন কিছু হারাম করার কোন অধিকার কারো নেই। যদি কেউ তা করার দুঃসাহস করে তাহলে বুঝবে হবে সে আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমা লংঘন করছে। দ্বীনী আইন-বিধান প্রণয়নে আল্লাহ্র নিরংকুশ অধিকারকে যারা কেড়ে নিতে চাচ্ছে, তাদের এ কাজকে যারা খুশি মনে মেনে নেবে ও গ্রহণ করবে, অনুসরণ করবে, তারা আল্লাহর সাথে তাদের শরীক করার মতো মারাত্মক অপরাধ করবে। শিরকের এ অপরাধ আল্লাহ্ কিছুতেই ক্ষমা করবে না। সূরা আশ-শুরার পূর্বোদ্ধৃত আয়াতটি এখানেও পঠিতব্যঃ
أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ.
ওদের কি এমন শরীক বা উপাস্য আছে নাকি, যারা ওদের জন্যে দ্বীনের এমন বিধান রচনা করে দিচ্ছে, যার জন্যে আল্লাহ্ কোন অনুমতিই দেন নি? ইয়াহূদী ও খ্রীস্টানরা হালাল-হারাম নির্ধারণের নিরংকুশ কর্তৃত্ব দিয়েছিল তাদের পাদ্রী ও পণ্ডিতদের। কুরআন মজীদ এ দিকে ইঙ্গত করেই বলেছেঃ
اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا ۖ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ
ওরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে ওদের পাদ্রী-পণ্ডিতদের খোদা বানিয়ে নিয়েছে আর ঈসা মসীহ্কে। অথচ ওদের নির্দেশ দেয়া হয়েছিল কেবলমাত্র এক আল্লাহ্র দাসত্ব ও বন্দেগী করতে। আসলে সে আল্লাহ্ ছাড়া ইলাহ আর কেউ নয়- নেই। তিনি সর্বাত্মকভাবে পবিত্র, ওদের শিরকের অনেক ঊর্ধ্বে তিনি। (সূরা তাওবাঃ ৩১)
আলী ইবনে হাতিম পূবে খ্রীস্ট ধর্ম অবলম্বনকারী ছিলেন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করে যখন দেখতে পেলেন, নবী করীম সা. উক্ত আয়াত পড়ছেন, তখন তিনি বললেনঃ
............ আরবী .................
হে রাসূল! ওরা তো ওদের পাদ্রী-পণ্ডিতদের ইবাদত করেনি?
রাসূলে কারীম সা. জবাবে বললেনঃ তাই নাকি? এ পাদ্রী-পণ্ডিতরাই তো ওদের জন্যে হালাল-হারাম নির্ধারণ করে দিয়েছে এবং ওরা তা-ই সাগ্রহে ঐকান্তিকভাবে মেনে নিয়েছে। আর কুরআনে এটাকেই বলা হয়েছে ওদের ‘ইবাদত’ অর্থাৎ এরূপ করাই ইবাদত। ‘ইবাদত’ বলতে যা বোঝায়, তা ওরা করেছে সেই পাদ্রী-পণ্ডিতদের। [তিরমিযী প্রভৃতি]
অপর একটি বর্ণনায় বলা হয়েছে, নবী কারীম সা. উপরিউক্ত আয়াতটির ব্যাখ্যা দান পর্যায়ে বলেছেনঃ
................. আরবী .................
ওরা ওদের পাদ্রী-পণ্ডিতদের বন্দেগী করত না, এ কথা কি সত্য? কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার এই যে, এ পাদ্রী-পণ্ডিতরা যখন কোন জিনিসকে তাদের জন্যে হালাল ঘোষণা করত, তখন তারাও সেটাকে হালালরূপে গ্রহণ করে নিত এবং অনুরূপভাবে যখন ওরা তাদের জন্যে কোন জিনিসকে হারাম বলে দিত, অমনি তারা সেটাকে হারাম মেনে নিত। বস্তুত কাউকে এরূপ অধিকার বা মর্যাদা দানই হচ্ছে তার ইবাদত করা।
খ্রীস্টানরা চিরকাল এ বিশ্বাসই পোষণ করে আসছে যে, হযরত ঈসা মসীহ্ আ. ঊর্ধ্বলোকে চলে যাওয়ার পূর্বে তাঁর ছাত্র-সাগরিদদের হালাল-হারাম করার পূর্ণ কর্তৃত্ব দিয়ে গেছেন। তারা নিজেদের ইচ্ছেমত হালাল-হারাম ঘোষণা করতে পারে। ইঞ্জিল মথি গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছেঃ
আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, তোমরা পৃথিবীতে যাহা কিছু বন্ধ করিবে, তাহা স্বর্গে বন্ধ হইবে এবং পৃথিবীতে যাহা কিছু মুক্ত করিবে, তাহা স্বর্গে মুক্ত হইবে।
মুশরিকদের সম্পর্কে কুরআন মজীদে বলা হয়েছে- তারা আল্লাহ্র অনুমতি ব্যতিরেকে নিজরোই হালাল-হারাম নির্ধারণ করেছে।
ইরশাদ করা হয়েছেঃ
قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ ۖ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ
তোমরা কি ভেবে দেখেছ, আল্লাহ্ তোমাদের রিয্ক যে দিয়েছেন, তার মধ্যে হালাল-হারাম তোমরা নির্ধারিত করে নিয়েছে? বল, আল্লাহ কি তোমাদের তা করার অনুমতি দিয়েছেন, না তোমরা আল্লাহ্র নামে মিথ্যা কথা বানিয়ে বলেছ? (সূরা ইউনূসঃ ৫৯)
আল্লাহ আরও বলেছেনঃ
وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَٰذَا حَلَالٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ
তোমাদের মুখে যা আসে তা-ই বলে দিও না- এটা হালাল ও এটা হারাম। এতে আল্লাহর নামে সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা চালানো হবে। আর যারাই আল্লাহ্র নামে এ ধরণের মিথ্যা কথা প্রচার করে, তারা কখনই কল্যাণ বা সাফল্য লাভ করতে পারে না। (সূরা নহলঃ ১১৬)
এ সব সুস্পষ্ট অকাট্য আয়াত ও হাদীসসমূহ থেকে নিঃসন্দেহে জানতে ও বুঝতে পারা যায় যে, হালাল-হারাম নির্ধারণ ও ঘোষণার একমাত্র অধিকার মহান আল্লাহ্র। একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া এ অধিকার অন্য কারো নেই, থাকতে পারে না। তিনি নিজেই এ কাজ করেছেন এবং তা তিনি তাঁর নিজের কালাম কুরআন মজীদে বলে দিয়েছেন, না হয় তাঁর নবী-রাসূলের বাণীতে ঘোষণা করিয়েছেন। হালাল-হারাম করণ পর্যায়ে আল্লাহ্র সিদ্ধান্তকে লংঘন করার কোন অধিকারই কারো নেই। ফিকাহবিদগণ তা করেনও নি। কুরআন মজীদে বলেই দেয়া হয়েছেঃ
وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ
আল্লাহ যা কিছু তোমাদের জন্যে হারাম করেছেন তা তিনি নিজেই সুস্পষ্ট ও ভিন্ন ভিন্ন করে তোমাদের জন্যে বলে দিয়েছেন। (সূরা আন’আমঃ ১১৯)
বস্তুত হালাল-হারাম নির্ধারণও কি জায়েয, কি নাজায়েয, তা মৌলিকভাবে ও নিজস্ব মর্জি অনুযায়ী চিহ্নিত করার কোন অধিকার বা কর্তৃত্বই ফিকাহবিদদের নেই। কেননা এটা তো দ্বীনী শরীয়ত রচনা পর্যায়ের কাজ। ফিকাহবিদগণ ইজতিহাদ করতে পারেন, শরীয়তের ব্যাপারে তাঁদের মতামত- নেতৃত্ব স্বীকৃতব্য। তা সত্ত্বেও তাঁরা কোন বিষয়ে ফতোয়া দিতে রীতিমত ভয় পেতেন। একজনের কাছে ফতোয়া চাওয়া হলে তিনি অন্য জনের কাছে যেতে বলে নিজে এ কাজ এড়িয়ে যেতেন। কেননা তাঁদের ভয় ছিল, এ কাজ করতে গিয়ে কোন ভুল করে বসতে পারেন, হালালকে হারাম বা এর বিপরীত করার অপরাধ হয়ে যেতে পারে। আর তা করা কিছুতেই উচিত হতে পারে না।
ইমাম শাফঈ তাঁর (আরবী) গ্রন্থে ইমাম আবূ হানীফার ছাত্র কাযী আবূ ইউসূফের কথা উদ্ধৃত করেছেন। তিনি বলেছেনঃ
‘আমি বিপুল সংখ্যক সুবিজ্ঞ সুবিজ্ঞ ও দ্বীন পারদর্শীদের দেখেছি। তাঁরা ফতোয়া দেয়া পছন্দ করেন না। কোন জিনিসকে তাঁরা সরাসরি হালাল বা হারাম বলার পরিবর্তে কুরআনে যা আছে, কোনরূপ ব্যাখ্যা ছাড়া তা বলে দেয়াকেই যথেষ্ট মনে করতেন। বিশিষ্ট তাবেয়ী আলেম ইবনুস সায়েব বলেছেনঃ তোমরা সে রকম লোক হবে না যে বলে, আল্লাহ্ অমুক জিনিসটি হালাল করেছেন কিংবা এটা আল্লাহর খুব পছন্দ। কেননা কিয়ামতের দিন আল্লাহ বলবেন, ‘না আমি ওটাকে হালাল করেছিলাম, আর না ওটা আমার পছন্দ ছিল।’ তেমনি সে ব্যক্তির মতও যেন তোমার অবস্থা না হয়, যে বলে ‘অমুক জিনিসটা আল্লাহ হারাম করে দিয়েছেন। কিন্তু কিয়ামতের দিন আল্লাহ বলবেন, ‘তুই মিথ্যাবাদী, আমি তো ওটাকে হারাম করিনি, ও কাজ করতে নিষেধও করে দেইনি। কূফার প্রখ্যাত তাবেয়ী ফিকাহ্ বিশারদ ইবরাহীম নখয়ী সম্পর্কে উদ্ধৃত হয়েছে, তাঁর ছাত্র-শাগরিদগণ যখন ফতোয়া দিতেন, তখন, এটা মাকরূহ কিংবা এতে কোন দোষ নেই, প্রভৃতি ধরণের কথা বলতেন। কেননা কোন জিনিসকে হালাল বা হারাম বলে নির্ধারণ করার মত দায়িত্বহীন কাজ আর কিছু হতে পারে না।
শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া বলেছেনঃ
............... আরবী ..............
যে জিনিসটার হারাম হওয়ার কথা নিশ্চিত-নির্দিষ্ট-অকাট্যভাবে জানা গেছে, কেবলমাত্র সেই জিনিসটা ছাড়া অন্য কোন জিনিসের ক্ষেত্রে প্রাথমিক কালের মনীষীগণ কখনও হারাম শব্দটি প্রয়োগ করতেন না।
অনুরূপভাবে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল র.- কে কোন বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলে জবাবে তিনি বলতেনঃ আমি ওটাকে মাকরূহ মনে করি অথবা আমি ওটাকে ভাল মনে করি না বা পছন্দ করি না’। ইমাম মালিক, ইমাম আবূ হানীফা ও অন্যান্য ইমামদের সম্পর্কেও এ কথাই সত্য।
৩. হালালকে হারাম ও হারামকে হালালকরণ শির্ক পর্যায়ে অপরাধ
যে সব লোক নিজ নিজ স্বভাবে হালাল-হারামকরণের অধিকারী বলে নিজেদের মনে করে, ইসলাম তাদের বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করেছে। বিশেষভাবে হালালকে যারা হারাম বলে, তাদের ওপর ইসলামের আক্রমণ অত্যন্ত কঠোর। কেননা এর ফলে মানুষ অকারণ সংকীর্ণতা ও কৃচ্ছ্রতার মধ্যে পড়ে যায়, অথচ আল্লাহ্ তো বিপুল প্রশস্ততা দান করেছেন। এরূপ নীতির ফলে লোকদের মনে ভিত্তিহীন কৃচ্ছ্রতা ও সূক্ষ্ণতা অবলম্বনের প্রবণতা প্রবল হয়ে উঠে অথচ নবী করীম সা. এ কৃচ্ছ্রতা সূক্ষ্ণতি সূক্ষ্ণতার প্রবণতাকে কঠোর ভাষায় পরিহার করে চলতে বলেছেন। এ নীতি অবলম্বনকারীদের প্রতি তিনি তীব্র ঘৃণা প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেনঃ
................ আরবী ..............
সাবধান! দ্বীন-ইসলামের খুঁটিনাটি ব্যাপারে কঠোরতাকারীরা ধ্বংস হয়ে গেছে ধ্বংস হয়ে গেছে.. ধ্বংস হয়ে গেছে। (মুসলিম, আহমাদ, আবূ দাউদ)
তিনি মুহাম্মাদী রিসালাতের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেনঃ
................ আরবী ..............
আমি এমন এক দ্বীনসহ প্রেরিত হয়েছি, যা একমুখী, ঐকান্তিক ও সুপ্রশস্ত।
বস্তুত দ্বীন ইসলাম যে আকীদা-বিশ্বাস ও তওহীদ-স্রষ্টাকে সর্বদিক দিয়ে এক ও অংশীদারহীন মান্য করার ব্যাপারে একক আদর্শবাদী এবং শরীয়াত ও কর্মবিধানের ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদার ও প্রশস্ত, তাতে কোনই সন্দেহ নেই। শিরক এবং হালালকে হারাম করণের কাজটি তার সম্পূর্ণ পরিপন্থী।
একটি হাদীসে নবী কারীম সা. জানিয়েছেন, আল্লাহ তা’আলা ইরশাদ করেছেনঃ
................... আরবী ....................
আমি আমার বান্দাদের একমুখী ঐকান্তিক আদর্শের ওপর সৃষ্টি করেছি। কিন্তু শয়তানেরা তাদের প্ররোচিত ও বিভ্রান্ত করেছে। তাদের ওপর সেসব জিনিসকে হারাম করে দিয়েছে, যা আমি হালাল করেছিলাম। তাদের হুকুম দিয়েছে আমার সাথে এমন কিছুকে শরীক বানাবার, যাদের আমার সাথে শরীক হওয়ার কোন সনদ আমি কখনোই নাযিল করিনি। (মুসলিম)
এ থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো যে, হালালকে হারাম বলা শিরক পর্যায়ের কাজ। আরব মুশরিকরা যে শিরক করত, মূর্তিপূজা করত, ক্ষেত-ফসল ও জন্তু-জানোয়ারের ন্যায় পবিত্র জিনিসগুলোকে নিজেদের জন্যে হারাম বানিয়ে নিয়েছিল, কুরআন মজীদ সেজন্যে তাদের প্রতি তীব্র রোষ প্রকাশ করেছে। কেননা এগুলো সম্পর্কে আল্লাহ্ তা’আলা কোন সনদ বা সমর্থন নাযিল করেন নি। বহীরা, সায়েরা, অসীলা ও হাম- এসবই ছিল তাদের হারাম করা জন্তুগুলোর নাম। উষ্ট্রী পাঁচটি বাচ্চা প্রসব করলে ও শেষ বাচ্চাটি পুরুষ হলে এ মুশরিকরা সে উষ্ট্রীটির কান কেটে দিত। তার পৃষ্ঠে সওয়ার হওয়া নিষিদ্ধ ঘোষণা করে তাদের উপাস্য দেবদেবীদের উদ্দেশ্যে মুক্ত করে দিত। অতঃপর সে উষ্ট্রীটিকে যবেহ করা বা তার ওপর বোঝা চাপানো সবই সম্পূর্ণ হারাম বলে ঘোষণা করত। পানি-ঘাট কিংবা চারণভূমি থেকে সেটাকে তাড়ানও সম্ভবপর হতো না। এ উষ্ট্রীটির নাম দিত ‘বহীরা’ অর্থাৎ কান কাটা উষ্ট্রী। ‘সায়েরা’ বলা হতো সে উষ্ট্রীটিকে যেটিকে তার মালিক বিদেশ সফর থেকে ফিরে এসে বা রোগমুক্তি লাভ করে দেবতাদের নামে উৎসর্গ করে ছেড়ে দিত। ছাড়ী স্ত্রী ছানা প্রসব করলে নিজের অধিকারের মনে করত। আর পুরুষ ছানা প্রসব করলে মনে করত ওটার ওপর দেবতাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। আর পুরুষ স্ত্রী উভয় ধরণের ছানা প্রসব করলে পুরুষ ছানাকে দেবতাদের উদ্দেশ্যে বলিদানের পরিবর্তে সেটাকে মুক্ত করে দিত। তখন সেটার নাম হত ‘অসীলা’। আর যে উষ্ট্রীর শাবকের শাবক বোঝা বহনের উপযুক্ত হতো সে বৃদ্ধা উষ্ট্রীকে বোঝা বহন ও সওয়ারীর কাজে ব্যবহার করা নিষিদ্ধ হয়ে যেত। এটারই নাম হতো ‘হাম’।
এভাবে এ জন্তুগুলোকে হারাম মনে করাকে কুরআন মজীদ তীব্র ভাষায় প্রতিবাদ করেছে। পিতৃ পুরুষদের অন্ধ অনুসরণ করতে গিয়ে এ ধরণের কাজ করা যে কোনক্রমেই উচিত নয়, তা কুরআন মজীদ সুস্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছে। বলা হয়েছেঃ
مَا جَعَلَ اللَّهُ مِن بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ ۙ وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۖ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ - وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ۚ أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ -
আল্লাহ্ বহীরা, সায়েরা, অসীলা এবং হাম প্রভৃতি কিছুই বানান নি। এ কাফিররা আল্লাহ্র নামে মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছে। ওদের অধিকাংশই নির্বোধ। ওদের যখনই আহ্বান করা হয় যে, আল্লাহ্র নাযিল করা বিধান গ্রহণ কর এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর, তখন ওরা বলে যে, আমাদের বাপ-দাদার কাছ থেকে পাওয়া রীতিনীতিই আমাদের জন্যে যথেষ্ট। অথচ ওদের বাপ-দাদারা কিছুই জানত না, সত্য পথ-প্রাপ্তও ছিল না তারা, তা সত্ত্বেও কি ওরা তাদের পথ অনুসরণ করে চলতে থাকবে। (সূরা মায়িদাঃ ১০৩-১০৪)
সূরা আল-আ’রাফ- এ প্রকৃত হারাম জিনিসগুলোর উল্লেখ করে বলা হয়েছেঃ
قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ
বল, আল্লাহ্, তাঁর বান্দাদের জন্যে যেসব সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছেন এবং যেসব পবিত্র রিয্কের ব্যবস্থা করেছেন, সে সবকে কে হারাম করে দিল? (সূরা আল-আরাফঃ ৩২)
قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ
বল, আমার রব্ব তো এসব জিনিস হারাম ঘোষণা করেছেন; নির্লজ্জতার কাজ, প্রকাশ্য বা গোপনীয় পাপ, অকারণ ও অন্যায় বাড়াবাড়ি, আর আল্লাহ্র সাথে শির্ক, যার সমর্থনে তিনি কোন সনদ নাযিল করেন নি। সেই সঙ্গে যা জানো না, তা আল্লাহ্র নামে বলা। (সূরা আল আ’রাফঃ ৩৩)
হালাল ও হারামকরণ সংক্রান্ত এ বিতর্ক মক্কী সূরাসমূহে উদ্ধৃত হয়েছে। তার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, কুরআনের দৃষ্টিতে এ ব্যঅপারটি ছোটখাটো ও খুঁটিনাটি বা গুরুত্বহীন নয়। বরং এটার সম্পর্ক ইসলামের মৌল নীতি ও সামগ্রিক আদর্শের সাথে।
মদীনা শরীফে মুসলমানদের মধ্যে কৃচ্ছ্রতা ও পবিত্র জিনিসগুলোকে নিজেদের ওপর হারাম করার প্রবণতা তীব্রভাবে দেখা দেয়। এ পর্যায়ে আল্লাহ্ তা’আলা অকাট্য ও সুস্পষ্ট আয়াত নাযিল করে তাদেরকে আল্লাহ্র নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে থাকতে ও সিরাতুল মুস্তাকীমের ওপের অবিচল হয়ে চলতে বলেছেন। তার ইরশাদ হচ্ছেঃ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ - وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ
হে ঈমানদার লোকেরা! আল্লাহ্ তোমাদের জন্যে যেসব পবিত্র দ্রব্য হালাল করেছেন, সে সবকে তোমরা ‘হারাম’ মনে করো না। আর সীমালংঘন করবে না। নিশ্চিত জানবে, সীমালংঘনকারীদের আল্লাহ্ আদৌ পছন্দ করেন না। আল্লাহ যেসব হালাল ও পবিত্র রিয্ক তোমাদের দান করেছেন তোমরা তা ভক্ষণ কর। সে সঙ্গে সেই আল্লাহ্কে ভয় করতে থাক, যাঁর প্রতি তোমরা ঈমানদার বলে দাবি করেছ। (সূরা মায়িদাঃ ৮৭-৮৮)
৪. হারাম জিনিস ক্ষতিকর
আল্লাহ্ তা’আলা সমগ্র মানুষের সৃষ্টিকর্তা। তিনি মানুষকে এতসব অমূল্য নিয়ামত দান করেছেন, যার কোন হিসাব-নিকাশ করা সম্ভবপর নয়। তাই স্বভাবতই তাঁর অধিকার রয়েছে মানুষের জন্যে কোন কিছুকে হারাম বা হালাল ঘোষণা করার। এ ব্যাপারে কারো কোন প্রশ্ন করার বা আপত্তি জানাবার কোন অধিকারই থাকতে পারে না। তিনি রব্ব- এ হিসেবেই তাঁর এ অধিকার। মানুষ তাঁরই বান্দা। এ বান্দাহ হিসেবেই মানুষ তাঁর এ অধিকার মেনে চলতে বাধ্য। ঠিক যেমন রব্ব হিসেবেই তিনি মানুষকে নিজের বান্দা বানিয়েছেন এবং পালন করে চলার জন্যে দিয়েছেন জীবন-বিধান ও নিয়মতন্ত্র। তবে আল্লাহ্ যেহেতু তাঁর বান্দাদের প্রতি অপরিসীম দয়াবান- এ কারণে তিনি এ ব্যাপারে কোন জবরদস্তিও যেমন করেন নি, তেমনি অযৌক্তিক বা বিবেক-বুদ্ধি পরিপন্থী কোন বিধানও দেন নি। তিনি অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গতভাবেই এক-একটা জিনিসকে হালাল বা হারাম ঘোষণা করেছেন। সার্বিকভাবে সমগ্র মানবতার মৌলিক কল্যাণ সাধনই এর চরম লক্ষ্য। এ কারণে তিনি মানুষের জন্যে কেবল পাক-পবিত্র, উত্তম-উৎকৃষ্ট জিনিসিই হালাল করেছেন এবং হারাম করেছেন যাবতীয় নিকৃষ্ট-নষ্ট-খারাপ-ক্ষতিকর দ্রব্যাদি।
প্রসঙ্গত বলা যায়, তিনি ইয়াহূদীদের প্রতি কিছু কিছু ভাল ও উৎকৃষ্ট জিনিসও হারাম করে দিয়েছিলেন। কিন্তু এটা ছিল স্বয়ং ইয়াহূদীদের নাফরমানীসূচক আচরণের শাস্তিস্বরূপ। কেননা ওরা আল্লাহ্র হালাল হারামের সীমাকে স্বেচ্ছাচারিতা করে লংঘন করেছিল। আল্লাহ্ সেই কথাই বলেছেন নিম্নোক্ত আয়াতেঃ
وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ ۖ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ۚ ذَٰلِكَ جَزَيْنَاهُم بِبَغْيِهِمْ ۖ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ
যারা ইয়াহূদী ধর্মমত গ্রহণ করেছে তাদের ওপর আমরা হারাম করে দিয়েছিলাম সবরকমের নখধারী পাখী, গরু-ছাগলের চর্বি- শুধু তা বাদে যা ওদের পৃষ্ঠে বা আঁতুরিতে কিংবা হাড়ের সঙ্গে লাগা আছে। আর তা তাদের বিদ্রোহাত্মক ভূমিকার প্রতিশোধ হিসেবেই আমরা তা করেছি। এরূপ করাতে আমরা নিঃসন্দেহে যথার্থ ও সত্যবাদীই ছিলাম। (সূরা আন’আমঃ ১৪৬)
ইয়াহূদীরা কি ধরণের বিদ্রোহাত্মক ভূমিকা অবলম্বন করেছিল, কুরআনের অপর এক সূরায় তা বলে দেয়া হয়েছে। আয়াতটি এইঃ
فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا - وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ
যারা ইয়াহূদী মত গ্রহণ করে জুলুম করেছে, এ জুলুমের কারণে আমরা তাদের প্রতি সে সব জিনিসই হারাম করে দিয়েছি, যা তাদের জন্যে হালাল করে দেয়া হয়েছিল। সে সঙ্গে তাদের এ অপরাধের কারণেও যে, তারা লোকদেরকে খুব বেশি বাধা দিত, তারা সুদ গ্রহণ করত অথচ তা থেকে তাদের নিষেধ করে দেয়া হয়েছিল, আর তারা অবৈধ উপায়ে লোকদের ধন-মাল ভক্ষণ করত। (সূরা আ্ন্ নিসাঃ ১৬০-১৬১)
উত্তরকালে আল্লাহ্ তা’আলা তাঁর সর্বশেষ ও নবী-রাসূল আগমন সমাপ্তকারী রাসূল সব মানুষের জন্যে পাঠালেন। মানবতা এ সময় পূর্ণবয়স্কতা ও পুরামাত্রায় বিবেক-বুদ্ধি লাভ করেছিল। তখন আল্লাহ্ তা’আলা অনুগ্রহ করে তাদের ওপর থেকে সাময়িকভাবে চালানো সেই হারামের দুর্বহ বোঝা দূর করে দিলেন। আহলি কিতাব লোকদের কাছে এ রিসালাতের পরিচয় ছিল-কুরআন মজীদে তার উল্লেখ করা হয়েছে এ ভাষায়ঃ
يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ
তারা তাদের কাছে রক্ষিত তওরাত ও ইঞ্জিলে তার কথা লিখিত দেখতে পায়। সে তাদের ভাল ভাল কাজের আদেশ করে, খারাপ কাজ থেকে নিষেধ করে, তাদের জন্যে পাকপবিত্র জিনিসসমূহ হালাল ঘোষণা করে। আর তাদের ওপর যে সব দুর্বহ বোঝা ও শৃঙ্খলাদি চাপানো ছিল, তা তাদের ওপর থেকে নামিয়ে দেয়। (সূরা আরাফঃ ১৫৭)
অতঃপর অপরাধের কাফ্ফারা স্বরূপ ভাল, পবিত্র, উত্তম দ্রব্যাদি হারাম করার পরিবর্তে ইসলামে অন্যান্য পন্থা ও উপায়ের ব্যবস্থা করে দেয়া হয়। গুনাহের কাফ্ফারার জন্যে খালেস তওবার ব্যবস্থা করা হয়। পানি যেমন করে ময়লা-আবর্জনা ধুয়ে মুছে সাফ করে দেয়, তওবাও ঠিক তেমনি গুনাহ্ মাফ করিয়ে দেয়। এ ছাড়া এমন অনেক কাজেরও বিধান দেয়া হয়েছে, যা খারাপ কাজকে নির্মূল করে দেয়। দান-সাদকা ও গুনাহের আগুন নির্বাপিত করে, যেমন করে পানি নিভিয়ে দেয় আগুন। এছাড়া চলমান জীবনে এমন অনেক দুঃখ-কষ্ট ও বিপদ-মুসীবত ভোগ করতে হয় যা বান্দার গুণাহ-খাতা ও ভুল-ভ্রান্তি শুষ্ক পত্র-পল্লবের মতই ঝরিয়ে দেয়। এ কারণে ইসলামের এ সত্য অকাট্য হয়ে দেখা দিয়েছে যে, তা যা কিছু হারাম করেছে, তা অবশ্যই খারাপ, নিকৃষ্ট ও ক্ষতিকর।
বস্তুত যা খুব বেশি ও সম্পূর্ণ ক্ষতিকর তার উপকারের তুলনায় তাকেই হারাম করে দিয়েছে। যার যা খালেসভাবে উপকারী ও কল্যাণকর তাকে হালাল করে দেয়া হয়েছে। মদ্য ও জুয়া প্রসঙ্গে কুরআন মজীদের এ কথাই বলা হয়েছেঃ
يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا
হে নবী! লোকেরা তোমার কাছে মদ্য ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। তুমি বল, ও দুটোতে বড় গুনাহ্ রয়েছে, যদিও ফায়দাও কিছু রয়েছে, আর ও দুটো কল্যাণের তুলনায় ক্ষতিই অনেক বেশি। (সূরা বাকারাঃ ২১৯)
এ প্রেক্ষিতে বলা যায়, ইসলামে হালাল কি- যখনই এরূপ প্রশ্ন করা হবে তখনই বলা যাবে পাক=পবিত্র কল্যাণকর দ্রব্যাদি অর্থাৎ সুস্থ মানব মন যেসব জিনিস ভাল ও উত্তম মনে করে এবং কোনরূপ আদত-অভ্যাসের বশবর্তী না হয়েও সব মানুষ মোটামুটিভাবে তা পছন্দ করে তা-ই হচ্ছে হালাল। কুরআন মজীদে বলা হয়েছেঃ
................. আরবী ...................
লোকেরা আপনাকে জিজ্ঞেস করে তাদের জন্যে কি কি হালাল করা হয়েছে। হে নবী আপনি বলে দিন, তোমাদের জন্যে হালাল করা হয়েছে সে সব জিনিসই, যা পবিত্র-পরিচ্ছন্ন ও উত্তম-উৎকৃষ্ট।
অন্যত্র বলা হয়েছেঃ
.............. আরবী .................
আজ তোমাদের জন্যে হালাল করে দেয়া হয়েছে সেসব জিনিসই যা পাক-পবিত্র পরিচ্ছন্ন-উৎকৃষ্ট-ভাল।
যে কারণে আল্লাহ্ তা’আলা কোন জিনিসকে হারাম ঘোষণা করেছেন তা হচ্ছে সে জিনিসের নিকৃষ্টতা, খারাবি ও ক্ষতিকারতা। আর তা সব মুসলমানকেই বিস্তারিতভাবে জানতে হবে এমন কোন কথা নেই। কেননা সেসব বিষয়ে সঠিক জ্ঞান সমানভাবে সকলেরই থাকে না। হয়ত কেউ কেউ জানতে পারে আর অনেকেরই তা অজানা থেকে যায়। অনেক সময় একটি জিনিসের দোষ ও নিকৃষ্টতা হয়ত এখনও প্রকাশিত হয়নি, পরবর্তীকালে তা অবশ্যই জানা যাবে। এ অবস্থায় ঈমানদার ব্যক্তিমাত্রেরই কর্তব্য আল্লাহ্র ঘোষণাকে অকুণ্ঠিত চিত্তে ও নিঃসংকোচে মেনে নেয়া। বলা যে, জানলাম ও মেনে নিলাম।
আল্লাহ্ তা’আলা শূকরের গোশ্ত হারাম করেছেন। মুসলিমরা শুধু এতটুকুই বুঝতে পারল যে, তা অত্যন্ত ঘৃণ্য ও খারাপ বলেই হারাম করা হয়েছে। কিন্তু কালের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান-বিজ্ঞানেরও অগ্রগতি ঘটে। তার ফলে জানা গেল যে, শূকরের গোশ্তে এক প্রকার ধ্বংসাত্মক ও মানব হত্যাকারী বিষাক্ত জীবাণূ রয়েছে। কিন্তু শূকরের গোশ্ত সংক্রান্ত এ জ্ঞান যদি নাও জানা যেত কিংবা এর চাইতে ভিন্নতর কিছুও জানা যেত তাহলেও মুসলিমদের আকীদা কখনও পরিবর্তন হতো না। কেননা আল্লাহ্র ঘোষণায় তা নাপাক ও অত্যন্ত খারাপ।
দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ্য, নবী করীম সা. ইরশাদ করেছেনঃ
................... আরবী ..................
তিনটি অভিশাপ আহ্বানকারী জিনিস থেকে তোমরা দূরে থাক। তা হচ্ছে পানি পানের স্থানে, রাস্তার মাঝখানে ও ছায়াচ্ছন্ন স্থানে পায়খানা করা। (আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ, হাকিম, বায়হাকী)
প্রাথমিককালে এ কথাটির তাৎপর্য শুধু এতটুকুই বোঝা গিয়েছিল যে, এ তিনটি স্থানে পায়খানা করা খুবই খারাপ কাজ- ভদ্রতা, শূচিতা ও সুস্থ বিবেক-বুদ্ধির পরিপন্থী। কিন্তু বৈজ্ঞানিক জ্ঞান বিকাশের ফলে উত্তরকালে আমরা জানতে পারলাম যে, এ কাজটি সাধারণ স্বাস্থ্যনীতির দৃষ্টিতে অত্যন্ত ক্ষতিকর। কেননা এ কাজের ফলে মারাত্মক ধরণের সংক্রামক রোগ ছড়িয়ে পড়তে পারে।
এ প্রেক্ষিতে বলা যায়, জ্ঞান-বিজ্ঞানের যতই বিকাশ ও অগ্রগতি সাধিত হবে, ইসলামী শরীয়তের বিধান রচনার মূলে নিহিত কারণ ও কল্যাণ-দৃষ্টি ততই বেশি উদ্ঘাটিত হতে থাকবে। হালাল-হারাম নির্ধারণের মৌল কারণ জানতে আর কিছুই বাকী থাকবে না। বস্তুত ইসলামী শরীয়তের মূলে রচয়িতার বিশ্বমানবতার প্রতি অকৃত্রিম কল্যাণ বিবেচনা নিহিত রয়েছে। আর তা হবেই না বা কেন? তা রচিত সে মহাজ্ঞানী, মহাবিজ্ঞানী অপরিসীম দয়াবান আল্লাহ্র। তাই কুরআন মজীদের বলা হয়েছেঃ
وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
কোন্টি বিপর্যয়কারী- খারাপ এবং কোন্টি কল্যাণকর- ভাল, তা আল্লাহ্ তা’আলা নির্ভুল ও সঠিকভাবে জানেন। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তোমাদের কঠিন কষ্টের মধ্যে নিক্ষেপ করতে পারতেন। (কিন্তু তিনি তা চান নি) নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ সর্বজয়ী- দুর্জয়, মহাবিজ্ঞানী। (সূরা বাকারাঃ ২২০)
৫. হালাল যথেষ্ট, হারাম অপ্রয়োজনীয়
বস্তুত ইসলাম এক মহাসৌন্দর্য মণ্ডিত জীবন বিধান। মানুষের জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের উদ্দেশ্যে তা নাযিল করা হয়েছে। এ বিধানে যদি কোন জিনিস হারাম ঘোষিত হয়ে থাকে, তবে তার পরিবর্তে কোন উৎকৃষ্টতর জিনিসকে হালাল করে দেয়া হয়েছে। অতীব উত্তম বিকল্প পেশ করা হয়েছে। সে বিকল্প এমনি যে, তার দ্বারা এক দিকে যেমন সমস্ত বিপর্যয় সৃষ্টিকারী জিনিসের পথ রুদ্ধ হয়ে যায় তেমনি অপর দিকে হারাম জিনিসের প্রতি মুখাপেক্ষিতা বা তার ওপর নির্ভরশীলতা নিঃশেষ হয়ে যায়। আল্লামা ইবনুল কাইয়্যেম র. এদিকে ইঙ্গিত করে বলেছেনঃ
ইসলাম পাশা খেলার মাধ্যমে ভাগ্য জানাকে হারাম করে দিয়েছে। তার পরিবর্তে ইস্তেখারার দো’আর ব্যবস্থা করে দিয়েছে। [ইসলাম মুসলমানদের শিখিয়েছে যে, কোন কাজ করার পূর্বে সে যেন পরামর্শ করে এবং ইস্তেখারা করে। ইরশাদ হয়েছে, ‘যে ইস্তেখারা করে সে ব্যর্থ হয় না এবং যে পরামর্শ করে, সে লজ্জিত হয় না। ‘ইস্তেখারা’র অর্থ, যে দুটি ব্যাপার নিয়ে সে দ্বন্দ্বে পড়েছে- কোন্টা করবে, সে যেন এ দুটির মধ্যে যেটি উত্তম সেটির সন্ধান পাওয়ার জন্যে আল্লাহ্র কাছে দো’আ করে। এজন্যে নামায ও দো’আ মাসুরার ব্যবস্থা করে দেয়া হয়েছে।]
ইসলাম সুদ খাওয়াকে হারাম করে দিয়েছে। তার পরিবর্তে মুনাফাপূর্ণ ব্যবসা বৈধ করে দিয়েছে।
জুয়া হারাম করেছে, তার পরিবর্তে ঘোড়া, উষ্ট্র ও তীরের সেসব প্রতিযোগিতা লব্ধ ধনমাল গ্রহণ জায়েয করেছে, যা শরীয়াতের পরিপন্থী নয়।
পুরুষদের প্রতি রেশম ব্যবহার হারাম করা হয়েছে। তার পরিবর্তে সূতা, পশম, কাতানের বিভিন্ন সৌন্দর্যময় পোশাক বৈধ করেছে।
জ্বিনা-ব্যভিচার ও পুংমৈথুন হারাম করেছে। তার পরিবর্তে বিবাহিতা স্ত্রীর সাথে যৌন সঙ্গম বৈধ করেছে।
মাদক দ্রব্য হারাম করা হয়েছে। তার পরিবর্তে দেহ ও মনের উপকারী সুস্বাদু পানীয় হালাল করে দিয়েছে।
খারাপ ও নিকৃষ্ট ধরণের খাদ্য হারাম করেছে। তার পরিবর্তে উত্তম উৎকৃষ্ট ও ভাল-ভাল খাদ্য হালাল করে দিয়েছেন।
এভাবে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ বিধানের পর্যালোচনা করা হলে প্রমাণিত হবে যে, আল্লাহ্ তা’আলা যদি একদিকে মানুষের জীবনে কোন কোন জিনিসকে হারাম করে সংকীর্ণ করে থাকেন তাহলে অপর দিকে বহু জিনিসকে হালাল করে জীবনকে বিপুল প্রশস্ততা ও উদারতা এনে দিয়েছেন। এক দিকের দুয়ার বন্ধ করে দিয়েছেন বটে, কিন্তু অপরদিকের দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। কেননা আল্লাহ্ তা’আলা মানব জীবনকে কোন দুরূহ কষ্ট ও কৃচ্ছ্রতার মধ্যে ফেলে দিতে চান নি। তাদের জন্যে স্বাচ্ছন্দ্যই তাঁর কাম্য। তিনি মানুষের জীবনকে কল্যাণ, নির্ভুল হেদায়াত ও রহমতে কানায় কানায় ভরে দিতে চেয়েছেন। আল্লাহ নিজেই জানিয়ে দিয়েছেনঃ
يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ - وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا - يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ ۚ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا
আল্লাহ চান যে, তিনি তোমাদের কাছে তাঁর আইন বিধান সুস্পষ্ট করে বলে দেবেন। তোমাদের জানিয়ে দেবেন অতীত হয়ে যাওয়া লোকদের হেদায়েতের নিয়ম ও পন্থাসমূহ। তিনি স্বীয় রহমত সহকারে তোমাদের প্রতি উন্মুখ। আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও সর্বজ্ঞানী। আল্লাহ তো তোমাদের প্রতি রহমতের আচরণ করতে চান, কিন্তু যারা নিজেদের কামনা-বাসনা-লালসার অনুসরণ করে চলেছে, তারা তোমাদের সত্যপথ থেকে বহু দূরে সরিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে। আল্লাহ তোমাদের ওপর থেকে দুর্বহ বোঝা লাঘব করতে চান। কেননা মানুষ তো দুর্বলতম সৃষ্টি। (সূরা নিসাঃ ২৬-২৮)
৬. হারাম কাজের নিমিত্তও হারাম
ইসলামের একটা মৌল নীতি হচ্ছে, যা হারাম কাজের হেতু, তাও হারাম। এভাবেই ইসলাম হারাম কাজ সঙ্ঘটিত হওয়ার কারণসমূহকেও হারাম করে দিয়েছে। কেননা এ কারণসমূহ বন্ধ না হলে আসল হারাম কাজটি অনুষ্ঠিত হতে কোনই অসুবিধা থাকবে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়- ইসলাম জ্বিনা বা ব্যভিচার হারাম করেছে। এ হারাম কাজকে সহজ, সুবিধাজনক ও অনিবার্য করে দেয় যেসব কারণ, ইসলাম তাকেও হারাম ঘোষণা করেছে। এ পর্যায়ের কাজের মধ্যে রয়েছে নারীদের অবাধ-উন্মুক্ত ও উচ্ছৃঙ্খল চলা-ফেরা, খারাপভাবে নারী-পুরুষের নিভৃত একাকীত্বে মিলিত হওয়া, অবাধ দেখা-সাক্ষাত, মেলামেশা, গোপন প্রেম-বন্ধুত্ব, নগ্ন ছবি, অশ্লীল পত্র-পত্রিকা ও যৌন উত্তেজন গান-বাজনা ইত্যাদি। এর কারণে ইসলামী শরীয়াত-পারদর্শিতাগণ মূলনীতি ঘোষণা করেছেনঃ
‘যা যা হারাম কাজ ঘটায় তা-ও হারাম।’
এ প্রেক্ষিতে ইসলামের অপর একটি মৌল নীতিও বিবেচ্য। তা হচ্ছে মূল হারাম কাজ যে করে, কেবল সে-ই সেজন্যে গুনাহ্গার ও অপরাধী গণ্য হয় না। এ কাজে যে লোক যতটুকু সহায়তা যুগিয়েছে সেও ততটুকু মাত্রয় গুনাহগার ও অপরাধী গণ্য হবে- এ সহায়তা-সহযোগিতা বস্তুগতভাবে হোক কিংবা শাব্দিকভাবে। মূল হারাম কাজে যে যতটুকু সাহায্য করেছে, মূল গুনাহে সে ঠিক ততটুকুই অংশীদার রয়েছে। এ কারণে নবী কারীম সা. কেবলমাত্র মদ্যপায়ীর ওপরই অভিশাপ বর্ষণ করেন নি, সে সঙ্গে মদ্য উৎপাদক, ব্যবস্থাপক, বহনকারী, যার জন্যে বহন করা হয়েছে সেই সকলের উপর- এমন কি তার মূল্য গ্রহণকারীর উপরও অভিশাপ বর্ষণ করেছেন। অনুরূপভাবে সুদ যে খায়, যে খাওয়ায়, যে তার দলিল লেখে ও সাক্ষী হয়, এ এসব লোকই অভিশপ্ত। অতএব এ কাজটি হারাম কাজের সহায়ক, তাও হারাম। আর হারাম কাজে যে-ই যতটা সাহায্য করে সে ততটা এ গুনাহে শরীক হবে, তা কিছুমাত্র বিচিত্র নয়।
৭. হারাম কাজে কৌশল অবলম্বনও হারাম
যে সব বাহ্যিক কারণ মানুষকে হারাম কাজের দিকে টেনে নেয়, তাও যেমন হারাম, তেমনি গোপন করা- কৌশলের সাহায্যে কার্য সম্পাদনও হারাম। এ সব অপকৌশল শয়তানের প্ররোচনার ফল। ইয়াহূদীরা আল্লাহ্র হারাম করে দেয়া কাজ ও জিনিস কৌশলের মাধ্যমে হালাল বানিয়ে নিয়েছিল। এটা অত্যন্ত ঘৃণ্য। নবী করীম সা. ইরশাদ করেছেনঃ
.............. আরবী ...............
ইয়াহূদীরা যে কাজ করেছিল তোমরা তা করো না। আল্লাহ্ যা হারাম করেছেন, তা সামান্য কৌশলের সাহায্যে হালাল করতে যেয়ো না।
আল্লাহ তা’আলা ইয়াহূদীদের জন্যে শনিবারে কোনরূপ শিকার করতে নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু তারা কৌশল করে সে হারামকে হালাল বানিয়ে নিয়েছিল। তারা শুক্রবারে গর্ত খুড়ে রাখত, শনিবারে তাতে মাছ এসে জমা হয়ে থাকত আর রোববার দিন তারা তা ধরত। ওরা এরূপ কৌশল করাকে মোটেই অন্যায় মনে করত না। কিন্তু ইসলামী আইনবিদদের বিবেচনায় এরূপ করা সম্পূর্ণ হারাম। কেননা আসলে আল্লাহ চেয়েছিলেন তারা শিকার কার্য হতে বিরত থাকুক- তা প্রত্যক্ষভাবে হোক বা পরোক্ষভাবে।
কোন হারাম জিনিসের নাম বা তার বাহ্যিক আকৃতি পরিবর্তন করে দিলে এবং তার মূল অবস্থায় কোনরূপ পরিবর্তন না এসে থাকলে সে জিনিসটি হালাল হয়ে যাবে না এটা বরং হারামকে এড়ানর জন্যে একটা অপকৌশল মাত্র। লোকেরা যদি নতুন নতুন আকৃতির উদ্ভব করতে থাকে এবং সুদের ন্যায় একটা নাজায়েয কাজ করার জন্যে কৌশল অবলম্বন করে কিংবা মদ্যকে একটা ভাল নামে অভিহিত করে তা পান করতে শুরু করে দেয় তাহলেই তার হারাম ও গুনাহ হওয়ার কোনরূপ পার্থক্য সূচিত হবে না। রাসূলে কারীম সা. পূর্বেই সে বিষয়ে সতর্ক করে দিয়ে ইরশাদ করেছেনঃ
................. আরবী ...................
আমার উম্মতের মধ্য থেকে একদল লোক সূরার নাম পরিবর্তন করে তাকে হালাল করে নিতে চাইবে। (আহমদ)
লোকেরা যে নৈতিকতা বিধ্বংসী নৃত্যকে ‘শিল্প’ বা ‘ললিতকলা’ নামে অভিহিত করছে, ‘সূরাকে পানীয়’ বলছে, সুদকে মুনাফা (interest) নামে চিহ্নিত করছে, এটা কালের ঘাত-প্রতিঘাত ও আবর্তন-বিবর্তনেরই সুফল মাত্র নতুবা মূল কাজটির হারাম হওয়ার কোনরূপ পার্থক্য সঙ্ঘটিত হয়নি।
৮. নিয়ত ভাল হলেই হারাম হালাল হয় না
এ কথায় সন্দেহ নেই যে, ইসলাম শরীয়তী ব্যাপারাদিতে সদুদ্দেশ্য পরায়ণতা, দোষমুক্ত লক্ষ্য ও নিঃস্বার্থ মন-মানসিকতাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়। স্বয়ং নবী কারীম সা. বলেছেনঃ
............. আরবী .................
সমস্ত কাজের মূল্যায়ন হয় নিয়তের ভিত্তিতে। আর প্রত্যেক ব্যক্তি তা-ই পায়, যা সে ইচ্ছা করে। নিয়তের কারণেই মুবাহ্ ও আদত-অভ্যাস পর্যায়ের কার্যসমূহ ইবাদত ও আল্লাহ্র নৈকট্যলাভের কারণ হওয়ার যোগ্যতা লাভ করে। যে লোক খাদ্য গ্রহণ করে জীবন রক্ষা ও শান্তি অর্জনের জন্যে, যেন সে আল্লাহ্র জনগণের প্রতি কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনে সক্ষম হয়, তার এ খাদ্য-পানীয় গ্রহণও ইবাদত ও আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।
নিজের ও স্ত্রীর চরিত্র পবিত্র রাখা ও সন্তান লাভের উদ্দেশ্যে যে লোক নিজ স্ত্রীর সাথে সঙ্গম কাজে লিপ্ত হবে, তার এ কাজও ইবাদত পর্যায়ে গণ্য হবে এবং সে সওয়াবের অধিকারী হবে। এ প্রসঙ্গেই নবী সা. বলেছেনঃ
............... আরবী ..................
তোমাদের একজনের তার স্ত্রীর সাথে সঙ্গম কার্য করাও এক প্রকার সওয়াবের কাজ। সাহাবী গণ জিজ্ঞেস করলে, হে আল্লাহ্র রাসূল! একজন তার যৌন প্রবৃত্তি চরিতার্থ করল আর তাতেই সে সওয়াব পেয়ে যাবে? রাসূল বললেনঃ সে যদি হারাম সঙ্গমে লিপ্ত হতো, তাহলে কি সে গুনাহ্গার হতো না? অনুরূপভাবে সে বৈধ ও হালাল যৌন কর্মেও সওয়াব পাওয়ার অধিকারী হবে। (বুখারী, মুসলিম)
হাদীসে আরও উদ্ধৃত হয়েছেঃ
................. আরবী .................
যে ব্যক্তি দুনিয়ার হালাল জিনিসসমূহ অর্জন করতে চাইবে স্বীয় আত্মমর্যাদা রক্ষা, স্বীয় পরিবারবর্গের প্রয়োজন পূরণ ও নিজের প্রতিবেশীর প্রতি দয়াপরবশ হওয়ার উদ্দেশ্যে, সে আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাত করবে এরূপ অবস্থায় যে, তার মুখমণ্ডল পূর্ণিমা রাতের চাঁদের মত অত্যুজ্জ্বল ও আলোকমণ্ডিত হবে। (তাবারানী)
এভাবে মুমিন ব্যক্তি যে জায়েয কাজই করবে তা ভাল নিয়তের দরুন ইবাদত হয়ে যাবে। কিন্তু হারাম সর্বাবস্থায়ই হারাম থেকে যাবে, তা যত ভাল ও পবিত্র উদ্দেশ্যেই হোক না কেন, যতই বড় উত্তম ও উন্নত লক্ষ্য তার মূলে থাক না কেন। কোন উন্নত লক্ষ্য অর্জনের জন্যে হারাম পন্থা গ্রহণ ইসলাম আদৌ পছন্দ করে না।
কেননা ইসলাম লক্ষ্যের উচ্চতর, মহত্তর হওয়া এবং তার অর্জনের উপায় ও পন্থার পবিত্র হওয়া- এ দুটিই কাম্য। উদ্দেশ্য সর্ব প্রকারের উপায় ও পন্থাকে বৈধ করে দেয়- এ সুবিধাবাদী নীতি ইসলাম মেনে নিতে আদৌ প্রস্তুত নয়। উপরন্তু সঠিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের জন্যে বহু সংখ্যক ভুল পন্থা ও উপায় গ্রহণের প্রয়োজন আছে বলেও ইসলাম মনে করে না। পক্ষান্তরে সঠিক ও নির্ভুল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের জন্যে সঠিক নির্ভুল ও পবিত্র পন্থা ও উপায় অবলম্বন করাকে একান্তই জরুরী বলে মনে করে। কেউ যদি মসজিদ নির্মাণ বা জনকল্যাণমূলক কাজ করার উদ্দেশ্যে সুদ, ঘুষ, হারাম, খেলা-তামাসা, জুয়া ও অন্যান্য নিষিদ্ধ উপায়ে অর্থোপার্জন করে তাহলে তার এ ভাল উদ্দে্শ্য হারাম কাজের হারাম হওয়াটাকে পরিবর্তন করে হালাল করে দেবে না। কেননা ইসলামের উদ্দেশ্য, মনোভাব বা শুভ ইচ্ছা হারামের ওপর কিছুমাত্র প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। নবী করীম সা. এ শিক্ষাদান প্রসঙ্গে বলেছেনঃ
.............. আরবী ..............
আল্লাহ্ পবিত্র। তিনি পবিত্র জিনিসই কবুল করেন। ঈমানদার লোকদের তিনি সে আদেশই দিয়েছেন যার নির্দেশ তিনি দিয়েছিলেন, তাঁর নবী-রাসূলগণকে। বলেছেনঃ (কুরআনের আয়অত) হে রাসূলগণ! পবিত্র দ্রব্যসামগ্রী খাও ও নেক কাজ কর। তোমরা যা কিছুই কর, আমি সে বিষয়ে পূর্ণ অবহিত। (সূরা মুমিনূনঃ ৫১)
আরও বলেছেনঃ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ
হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা আমাদের দেয়া পবিত্র রিযিকসমূহ ভক্ষণ করো। (সূরা বাকারাঃ ১৭২)
অতঃপর রাসূল সা. বললেনঃ
............... আরবী .................
এক ব্যক্তি দীর্ঘ পথসফর করে। তার মাথার চুল এলোমেলো, উস্কো-খুস্কো, পদযুগল ধূলি মলিন। সে তার দুটি হাত উপরের দিকে তুলে বারবার দো’আ করে আল্লাহ, আল্লাহ! কিন্তু তার খাদ্য হারাম, পানীয় হারাম, পরিচ্ছদ হারাম- হারাম খাদ্যে সে লালিত পালিত হয়েছে। এহেন ব্যক্তির দো’আ আল্লাহর কাছে কি করে কবুল হতে পারে? (মুসলিম, তিরমিযী)
তিনি আরও বলেছেনঃ
............... আরবী. ...........
যে লোক হারাম মাল সঞ্চয় করল, পরে তা দান করে দিল, সে তার কোন সওয়াব পাবে না। তার হারাম উপার্জনের গুনাহ্ তো তার উপর বোঝা হয়ে চাপবেই।
.................. আরবী. ...............
বান্দা হারাম মাল উপার্জন করে যা দান-সাদ্কা করে, তা কবুল করা হবে না। তা থেকে সে ব্যয় করে তাতে বরকতও হয় না। আর যা পশ্চাতে রেখে যায়, তা তার জাহান্নামে যাওয়ার পাথেয় হয় মাত্র। সত্যি কথা হচ্ছে, আল্লাহ তা’আলা অন্যায়কে অন্যায় দ্বারা নির্মূল করেন না। বরং অন্যায়কে ন্যায় দ্বারা দূর করেন। আর আসলে ময়লা-আবর্জনা ময়লা-আবর্জনাকে দূল করতে পারে না।
৯. হারাম থেকে দূরে থাকার জন্যে সন্দেহপূর্ণ কাজ পরিহার
দুনিয়ার মানুষের প্রতি আল্লাহর বড় রহমত হচ্ছে এই যে, তিনি হালাল যেমন স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন, তেমনি হারামকেও চিহ্নিত করে দিয়েছেন।
وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ
তোমাদের প্রতি যা যা হারাম করা হয়েছে, আল্লাহ্ তা স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন। (আল আন’আমঃ ১১৯)
কাজেই যা সুস্পষ্টরূপে হালাল তা করায় কোন বাধা-প্রতিবন্ধকতা থাকতে পারে না। আর যা সুস্পষ্টরূপে হারাম, কোনরূপ উপায়হীন অবস্থা ভিন্ন সাধারণ ভাবে তা করার কোন অনুমতি দেয়া যেতে পারে না। এতদ্ব্যতীত এ সুস্পষ্ট হালাল ও সুপ্রকট হারামের মাঝখানে সন্দেহপূর্ণ জিনিসগুলোরও একটা পর্যায় রয়েছে। এগুলোর ব্যাপারে মানুষ দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়ে যায়। এগুলোর সন্দেহপূর্ণ হওয়ার কারণ হলো অনেক ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দলিল-প্রমাণ অস্পষ্ট থাকে কখনও প্রাপ্ত অকাট্য দলিলটি প্রয়োগ করার ব্যাপারে অকাট্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় না বলে মানুষ চরমভাবে সংশয়ের মধ্যে নিপতিত হয়ে পড়ে। এসব সন্দেহপূর্ণ জিনিস পরিহার করাকে ইসলামে বলা হয় আল্লাহ-ভীতি, তাকওয়া, অন্যায় থেকে বাঁচার জন্যে সতর্কতাবলম্বন। তা পাপ পথ বন্ধ করার কাজ করে। মানুষকে তা নির্ভুল প্রশিক্ষণ দেয়, সঠিক পথে পরিচালিত করে। অন্যথায় মুনষ সন্দেহপূর্ণ কাজের মধ্যে লিপ্ত হয়ে হারাম কাজের মধ্যে পড়ে যেতে পারে। নবী কারীম সা. নিজেই এ মৌল নীতি ঘোষণা করেছেনঃ
................. আরবী .....................
হালাল সুস্পষ্ট, হারামও সুস্পষ্ট। এ দুটির মাঝখানে কতিপয় জিনিস সন্দেহপূর্ণ। সেসব সম্পর্কে অনেক লোকেরই জানা নেই যে, আসলে তা হালাল না হারাম। এরূপ অবস্থায় যে ব্যক্তি স্বীয় দ্বীন ও স্বীয় মান-মর্যাদা রক্ষার জন্যে সেসব থেকে দূরে থাকে, সে নিশ্চয়ই নিরাপত্তা পেয়ে যাবে। কিন্তু যে ব্যক্তি তন্মধ্য থেকে কোন কিছুর সাথে জড়িয়ে পড়বে, তার পক্ষে হারামের মধ্যে পড়ে যাওয়া অসম্ভব নয়। যে ব্যক্তি নিজের জন্তুগুলোকে নিষিদ্ধ চারণভূমির আশে-পাশে চড়ায়, তার পক্ষে সে নিষিদ্ধ অঞ্চলের মধ্যে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তোমরা শোন, প্রত্যেক রাজা-বাদশাহরই একটি ‘সুরক্ষিত চারণভূমি’ থাকে। আরও শোন আল্লাহ্র হারাম করা জিনিসগুলোই তাঁর সংরক্ষিত চারণভূমি। (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী)
১০. হারাম সকলেরই জন্যে
ইসলামী শরীয়তে হারামের বিধান সাধারণ, নির্বিশেষ এবং সকলেরই জন্যে। কোন জিনিস এক দেশের লোকদের জন্যে হারাম আর অপর দেশের লোকদের জন্যে হালাল হবে কিংবা কৃষ্নাঙ্গের জন্যে নিষিদ্ধ হবে আর শ্বেতাঙ্গদের জন্যে তা অনুমোদিত হবে, ইসলামে এমনটা হতেই পারে না। কোন বিশেষ শ্রেণী বা গোষ্ঠীর লোকদের জন্যে হালাল হবে আর অন্যদের জন্যে তা নিষিদ্ধ হবে ইসলামে তা-ও সম্পূর্ণ অকল্পনীয়। ইসলামে পাদ্রী পুরোহিত পণ্ডিত বা রাজা-বাদশাহ-অভিজাত প্রভৃতি শ্রেণীর লোকদের জন্যে কোন বিশেষ মর্যাদা স্বীকৃত হয়নি। তারা নিজেদের বিশেষ মর্যাদার দোহাই দিয়ে একদিকে নিজেদের লালসা চরিতার্থ করবে আর অপর দিক জনগণের ওপর বিশেষণ ধরণের আধিপত্য বিস্তার করে থাকবে, তার কোন সুযোগই ইসলামে দেয়া হয়নি। এ দিক দিয়ে মুসলিমদেরও নেই কোন বিশেষ মর্যাদা বা অধিকার। মুসলিমদের জন্যে একটি জিনিস হালাল হবে, আর অন্যদের জন্যে সে জিনিসটিই হবে হারাম ইসলামে এমন কোন বিধান আদৌ স্থান পায়নি। কেননা আল্লাহ তা’আলা তো নির্বিশেষ সমস্ত মানুষের রব্ব। অনুরূপভাবে তাঁর দেয়া জীবন-বিধান- ইসলামী শরীয়াত নির্বিশেষে সমস্ত মানুষের জন্যে দিগ্দিশারী। কাজেই তাঁর শরীয়তের যে যে জিনিসকে হালাল করেছেন, তা নির্বিশেষে সমস্ত মানুষের জন্যে হালাল। পক্ষান্তরে যা যা হারাম করেছেন, তা সবই হারাম সকলের জন্যে এবং কিয়ামত পর্যন্ত।
দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, যেমন চুরি। তা সকলের জন্যেই হারাম। চোর মুসলিম হোক কি অমুসলিম- সব ক্ষেত্রেই সমান। চোরের পরিচয় যাই হোক তাকে হোক কি অমুসলিম-সব ক্ষেত্রেই সমান। চোরের পরিচয় যাই হোক তাকে অবশ্যই শাস্তি ভোগ করতে হবে অনিবার্যভাবে। রাসূলে কারীম সা. নিজেই এ নীতির বাস্তবায়ন করেছেন। তিনি ঘোষণা করেছেনঃ
................ আরবী ..................
আল্লাহ্র নামে শপথ! মুহাম্মাদ-কন্যা ফাতেমাও যদি চুরি করে তাহলে তার হাতও কর্তিত হবে। (বুখারী)
রাসূলে কারীম সা.- এর জীবদ্দশায় চুরির একটি ঘটনা সঙ্ঘটিত হয়। তাতে একজন মুসলিম ও একজন ইয়াহূদীর ওপর সন্দেহ হয়। মুসলিম ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজন ইয়াহূদী ব্যক্তির ওপর দোষ চাপাতে থাকে, অথচ প্রকৃত পক্ষে মুসলিম ব্যক্তিই চুরি করেছিল। এ অবস্থায় আল্লাহ্র কাছ থেকে ওহী নাযিল হয়ে নিরপেক্ষ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে এবং ইয়াহুদীকে নির্দোষ ঘোষণা করা হয়। ইরশাদ করা হয়ঃ
إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ ۚ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا - وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا - وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا -
এ কিতাব আমরা তোমার প্রতি সত্যতা সহকারে নাযিল করেছি, যেন তুমি লোকদের মধ্যে সে অনুযায়ী ফয়সালা ও প্রশাসন চালাতে পারে, যা আল্লাহ্ তোমাকে দেখিয়েছেন। তুমি খিয়ানতকারীদের পক্ষে ঝগড়াকারীদের পক্ষে ঝগড়াকারী হবে না। আর সে লোকদের পক্ষে ওকালতি করবে না যারা নিজেদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে। আল্লাহ খিয়ানতকারী ও পাপ-প্রবণ লোকদের আদৌ পছন্দ করেন না। (সূরা নিসাঃ ১০৫-১০৭)
ইয়াহূদীরা তাদের প্রতি অবতীর্ণ আল্লাহ্র কিতাবে অনেক রদবদল করেছিল ইচ্ছেমত। তারা এ সিদ্ধান্ত করেছিল যে, ইয়াহূদীদের প্রতি সুদ হারাম হবে তখন, যদি সে তার কোন ইয়াহূদী ভাইকে ঋণ দেয়। কিন্তু অ-ইয়াহূদীকে সুদ ভিত্তিক ঋণ দিতে কোন নিষেধ নেই, তা হারাম নয়। তাদের গ্রন্থে লিখিত রয়েছেঃ
তুমি তোমার ভাইকে সুদভিত্তিক ঋণ দিও না তবে ভিন্ন জাতির লোককে সুদভিত্তিক ঋণ দিতে পারে।
কুরআন মাজীদেও ইয়াহূদীদের এ দুষ্কৃতির উল্লেখ রয়েছে। তাতে বলা হয়েছেঃ
وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَّا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ
ওদের মধ্যে এমন সব লোকও রয়েছে, তোমরা যদি একটি মুদ্রাও তাদের কাছে আমানত রাখ, তাহলে তারা তা ফিরিয়ে দেবে না, যতক্ষণ না তুমি তাদের মাথার ওপর চড়ে বসবে। তার কারণ হচ্ছে, তারা বলেন, উম্মী (অ-ইয়াহূদী)- দের ব্যাপারে আমাদের কোন দায়িত্ব নেই। আর তারা বুঝে শুনেই আল্লাহ্র নামে এ মিথ্যা প্রচার করে বেড়াচ্ছে। (সূরা আলে-ইমরানঃ ৭৫)
তারা যে আল্লাহ্র নামে মিথ্যার প্রচার করেছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কেননা আল্লাহ্র বিধান ও শরীয়তের বিধান বিভিন্ন জাতির মধ্যে পার্থক্য করে না। বিশ্বাসঘাতকতাকে সব নবী-রাসূলের জবানীতেই আল্লাহ্ তা’আলা হারাম ঘোষণা করিয়েছেন। ইয়াহূদীদের এ ঝগড়াটা যে নিতান্তই হীন, নীচ ও সংকীর্ণ মন-মানসিকতার পরিণাম তাতে কোনই সন্দেহ নেই। কোন আসমানী দ্বীনে তার একবিন্দু স্থান থাকতে পারে না। কেননা উন্নতমানের নৈতিকতা ও সত্যবাদ সব সময়ই মানবিক ও নির্বিশেষ হয়ে থাকে। তাই একটা জিনিস কারো জন্যে হালাল আর কারো জন্যে হারাম হতেই পারে না। যেমন আমানত রক্ষা। তা তাদের কাছে উত্তম চরিত্রের বৈশিষ্ট্য বলে স্বীকৃত ছিল বটে; কিন্তু নির্বিশেষে নয়। তা ছিল বিশেষভাবে তাদের নিজস্ব গোত্রের পরস্পরের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু গোত্রের বাইরে ভিন্ন লোকদের সঙ্গে সব রকমের বিশ্বাসঘাতকতা শুধু বৈধই নয়, অত্যন্ত শ্রেয় কর্তব্য এবং প্রিয়।
এভাবে মানুষে মানুষে, গোত্রে-গোত্রে ও জাতিতে-জাতিতে বিভেদ সৃষ্টিকারী অনেক প্রাচীন ধর্মীয় ও আধুনিক বৈজ্ঞানিক মতের প্রচলন রয়েছে সর্বত্র। এগুলো যেমন অমানবিক, তেমনি প্রকৃত যুক্তির কষ্টিপাথরে অনুত্তীর্ণ। অতএব তা পরিহার্য।
১১. প্রয়োজন নিষিদ্ধকে বৈধ করে
ইসলামের হারাম করার ক্ষেত্র ও পরিধি অত্যন্ত সংকীর্ণ। কিন্তু তার পরও যা যা হারাম করেছে, তাতে অত্যন্ত কঠোরতা ও অনমনীয়তা অবলম্বন করা হয়েছে। হারাম কাজের দিকের প্রকাশ্য ও গোপনীয় পথসমূহও রুদ্ধ করে দিয়েছে। অতপর যা হারাম কাজের কারণ, তাকেও হারাম করা হয়েছে। যা হারাম কাজে সাহায্য ও সহায়তা করে, তার সুযোগ করে দেয়া, তাও ইসলামে হারাম বলে ঘোষিত হয়েছে। কৌশল করে কোন হারামকে হালাল করতে চেষ্টা করাকেও হারাম করে দেয়া হয়েছে। তবে মানুষের প্রকৃত প্রয়োজনের তাগিদকে ইসলাম অস্বীকার করেনি। মানুষের মানবিক দুর্বলতার প্রতিও একবিন্দু উপেক্ষা প্রদর্শন করা হয়নি। তাই প্রবল পরাক্রান্ত মাত্রার প্রয়োজন ও মানুষের স্বাভাবিক দুর্বলতার প্রতি লক্ষ্য রেখে- মৌল প্রয়োজন পূরণ পরিমাণ হারাম গ্রহণের অনুমতি দেয়া হয়েছে। কিন্তু সে অনুমতিও অবাধ নয়, শর্তহীন নয়। প্রয়োজন পূরণ ও ধ্বংস থেকে বাঁচার মৌল লক্ষ্য মাত্র। এ কারণে আল্লাহ্ তা’আলা মৃত জীব, রক্ত ও শূকরের গোশত খাওয়া হারাম ঘোষণা করার পর ইরশাদ করেছেনঃ
فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
যে ব্যীক্ত নিরূপায় হয়ে যাব, েসে নিজে ইচ্ছুক সীমালংঘনকারী না হয়ে যদি ওসব থেকে কিছু পরিমাণ ভক্ষণ করে, তাহলে তার কোন গুনাহ্ হবে না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ ক্ষমাশীল দয়াবান। (সূরা বাকারাঃ ১৭৩)
আল্লাহ্ তা’আলার কুরআনে এ অনুমতির কথা বারবার ঘোষণা করেছেন। আর এ কথা থেকেই ইসলামী আইন পারদর্শিগণ এ মূলনীতি গ্রহণ করেছেনঃ
‘প্রয়োজন নিষিদ্ধ জিনিসকেও বৈধ করে দেয়।’
কিন্তু এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে, এসব কয়টি স্থানেই নিরুপায় ব্যক্তির জন্যে ‘ইচ্ছুক ও সীমালঙ্ঘনকারী না হওয়ার’ শর্ত আরোপ করা হয়েছে। তার অর্থ এই যে, নিরুপায় হয়ে গেলে, হালাল খাদ্য না-পাওয়া গেলে, ক্ষুধার তাড়নায় প্রাণবায়ু উড়ে যাওয়ার আশংকা তীব্র হয়ে দেখা দিয়ে তখন ‘হারাম খাদ্য খাওয়া যাবে বটে; কিন্তু তার প্রতি লোভ, কামনা, স্বাদ-আস্বাদন ও তৃপ্তি অর্জন লক্ষ্য হতে পারবে না। আর দ্বিতীয়ত তা খেতে গিয়ে ন্যুনতম প্রয়োজন পরিমাণ খাওয়া যাবে, উদর পূর্তি করে খাওয়া যাবে না। এ শর্ত থেকে আইনবিদগণ আর একটি মূল নীতি নির্ধারণ করেছেন। আর তা হচ্ছেঃ
................... আরবী. ...............
প্রয়োজনই তার পরিমাণ (বা পরিমাণের সীমা) নির্ধারণ করে।
মানুষকে প্রয়োজনের নিকট নত হতে হয়, একথা ঠিক। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, মানুষ প্রয়োজনের নিকট সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করে দেবে, নিজের সত্তার রশি তার হস্তে সপে দেবে। তাকে তো হালালের সাথেই জড়িত হয়ে থাকতে হবে। তারই সন্ধানে তাকে দিন-রাত ব্যতিব্যস্ত হয়ে থাকতে হবে। প্রয়োজনের কারণে নিষিদ্ধ জিনিস সাময়িকভাবে ও ন্যূনতম প্রয়োজন-পরিমাণ গ্রহণের অনুমতি দেয়া হয়েছে, তাকেই যেন চিরদিন আকড়ে ধরে থাকতে চেষ্টা না করে এবং স্বাদ-আস্বাদনে নিমগ্ন হয়ে না পড়ে, তার প্রতি তীক্ষ্ণ ও সতর্ক দৃষ্টি রাখা একান্তই আবশ্যক।
প্রয়োজনের তীব্রতার ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ গ্রহণের অনুমতি দিয়ে ইসলাম তার মৌল ভাবধারারই বাস্তবতা প্রমাণ করেছে এবং তার নিজস্ব নীতি ও আদর্শের দৃষ্টি খুব সহজতার ব্যবস্থা করে দিয়েছে। এ থেকে আল্লাহ তা’আলার এ ঘোষণার সত্যতাই অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়েছেঃ
يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ
আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি সহজতা রক্ষা করতে চান। তোমাদের প্রতি কোনরূপ কঠোরতা করার তার কোন ইচ্ছাই নেই। (সূরা বাকারাঃ ১৮৫)
مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
আল্লাহ্ তোমাদেরকে কষ্ট ও সংকীর্ণতার মধ্যে নিক্ষেপ করতে চান না। বরং তিনি তোমাদের পবিত্র পরিচ্ছন্ন করতে এবং তোমাদের প্রতি তাঁর নিয়ামত দান সম্পূর্ণ করতেই ইচ্ছুক, যেন তোমরা শোকর কর। (সূরা মায়িদাঃ ৬)
يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ ۚ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا
আল্লাহ্র তোমাদের বোঝা হালকা করতে চান। কেননা মানুষ তো দূর্বল অক্ষম সৃষ্টি হয়েছে। (সূরা নিসাঃ ২৮)
দ্বিতীয় অধ্যায়
মুসলিমের ব্যক্তিগত জীবনে হালাল-হারাম
- খাদ্য ও পানীয়
- পোশাক ও অলংকার-সৌন্দর্য
- ঘর-বাড়ি
- উপার্জন ও পেশা
মুসলিমের ব্যক্তিগত জীবনে হালাল-হারাম
খাদ্য ও পানীয়- বিশেষ করে পশুকুলের মধ্য থেকে খাদ্য গ্রহণ ব্যাপারে প্রাচীনতম কাল থেকেই জাতিসমূহের মধ্যে মতবিরোধ বা মতপার্থক্য চলে এসেছে। কোন্ কোন্ জিনিস জায়েয ও বৈধ এবং কোন্ কোন্ জিনিস নয়, এই নিয়েই মতবিরোধ দানা বেঁধে উঠেছে।
উদ্ভিজ খাদ্য ও পানীয়র ক্ষেত্রে মতবিরোধ খুব বেশি এবং ব্যাপক নয়। ইসলাম মদ্যপান হারাম করে দিয়েছে, তা আঙ্গুর দিয়ে বানান হোক, বা খেজুর, যব কিংবা অন্যকিছু দিয়ে। অনুরূপভাবে যেসব জিনিস মানুষের বিবেক-বুদ্ধি বিকৃত করে দেয় অথবা কোনরূপ বিপর্যয়ের সৃষ্টি করে, আর যা স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর তা সবই হারাম।
তবে পশু জাতীয় খাদ্যের ব্যাপারে দুনিয়ার বিভিন্ন জাতির মধ্যে তীব্র মতবিরোধ রয়েছে।
ব্রাহ্মণদের দৃষ্টিতে পশু যবাই করা ও খাওয়া
ব্রাহ্মণ ইত্যাদি ধর্মবিশ্বাসী ও কোন কোন দার্শনিক মতাবলম্বীদের দৃষ্টিতে পশু যবাই করা ও খাওয়া তাদের নিজেদের জন্যে হারাম। উদ্ভিদ বা শাক-সব্জিই তাদের একমাত্র খাদ্য। কেননা তাদের মতে পশু যবাই করা নিতান্তই মর্মান্তিক ও নির্দয়তার কাজ। ওদেরও বাঁচার অধিকার আছে এবং সে অধিকার থেকে বঞ্ছিত করা যেতে পারে না।
কিন্তু বিশ্ব প্রকৃতির ওপর দৃষ্টিপাত করলে ও গভীর সূক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বিবেচনা করলে স্পষ্ট বুঝতে পারা যায় যে, পশু যবাই করা একান্তই নির্দোষ কাজ। কেননা দুনিয়ার এসব জন্তু-জানোয়ার কোন নিজস্ব স্বতন্ত্র উদ্দেশ্যমূলক সৃষ্টি নয়। ওদের বুদ্ধি-বিবেক ও নিজস্ব ইচ্ছা ও বাছাই করার শক্তি বলতে কিছু নেই। ওদের স্বাভাবিক দেহ সংস্থা স্বতঃই প্রমাণ করে যে, ওরা মূলত মানুষের খেদমতের কাজ সুসম্পন্ন করার উদ্দেশ্যেই সৃষ্ট ও নিয়োজিত। মানুষ ওগুলোকে নিয়ন্ত্রণে এনে অনেক কার্য সম্পাদন করে। অনুরূপভাবে ওদের যবাই করে ওদের খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করা হলে তাতে আপত্তির কিছুই থাকতে পারে না। সৃষ্টিলোকে সদা কার্যকর আল্লাহ্র প্রদত্ত নিয়ম হচ্ছে, নিকৃষ্ট ও নীচ সৃষ্টি উত্তম ও উচ্চতর সৃষ্টির জন্য আত্মাহুতি দিচ্ছে। অনুরূপই জন্তু-জানোয়ার মানুষের খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে নিরন্তন। অনুরূপই জন্তু-জানোয়ার মানুষের খাদ্যে পরিণত হচ্ছে। শুধু তাই নয়, মানব সমষ্টির নিরাপত্তার জন্যে ব্যক্তিকে হত্যা করা একটি স্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে রয়েছে। মানুষের জন্য পশু যবাই করা না হলে ওরা যে মৃত্যু ও ধ্বংস থেকে রক্ষা পেতে পারছে, এমন তো নয়। অন্যান্য অধিক শক্তিশালী হিংস্র জন্তু-দানব কর্তৃক ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে ওদের খাদ্যে পরিণত হওয়া তো অবধারিত। অথবা ওরা স্বাভাবিক মৃত্যু বরণ করতে বাধ্য হবে। আর তা ওদের গলদেশে শানিত অস্ত্র চালিয়ে যবেহ করার তুলনায় অধিক কষ্টদায়ক হওয়া নিশ্চিত।
ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানদের দৃষ্টিতে হারাম জন্তু
আসমানী কিতাবে বিশ্বাসীদের মধ্যে ইয়াহুদীদের প্রতি স্থল ও জলভাগের বহু জন্তু-জানোয়ারকে হারাম করে দেয়া হয়েছে। পুরাতন নিয়ম-এর লাভী পরিভ্রমণের একাদশ অধ্যায়ে তার বিস্তারিত বিবরণ উদ্ধৃত হয়েছে। এই পর্যায়ে কিছু কিছু কথা কুরআন মজীদেও উল্লেখ করা হয়েছে। ইয়াহূদীদের প্রতি যা যা হারাম করা হয়েছিল, তা এ থেকে জানা যায়। আর এই হারামকরণ কেবল যে তাদের নিজেদের জুলুম ও বিদ্রোহমূলক কার্যকলাপের কারণে শাস্তিদানের উদ্দেশ্যেই হয়েছিল, তা স্পষ্ট করেই বলে দেয়া হয়েছে। ইরশাদ হয়েছেঃ
وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ ۖ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ۚ ذَٰلِكَ جَزَيْنَاهُم بِبَغْيِهِمْ ۖ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ
আর যারা ইয়াহুদী হয়েছে তাদের প্রতি আমরা সব নখ্ধারী জন্তু হারাম করে দিয়েছিলাম। আর গরু ও ছাগলের চর্বিও- ওদের পৃষ্ঠ ও অন্ত্রের সাথে কিংবা অস্থির সাথে জড়িত, তা ছাড়া এ কাজটি করা হয়েছে তাদের আল্লাহ বিরোধী শাস্তিস্বরূপ। আর তা করায় আমি যথার্থ ভূমিকা গ্রহণকারী নিঃসন্দেহে। (সূরা আন’আমঃ ১৪৬)
এ হচ্ছে ইয়াহুদীদের সম্পর্কিত ব্যাপার। খ্রিস্টানদের ব্যাপারটি অনুরূপই বটে। কেননা এক্ষেত্রে তারা ইয়াহুদীদেরই অধীন। কেননা ইনজিল এ নির্দেশকে নাকচ করে দেয়নি। বরং ঘোষণা করেছেঃ ‘ঈসা মসীহ পূর্ববর্তী শরীয়ত নাকচ করা রজন্য আসেন নি। বরং এসেছে তাকে পূর্ণত্ব দানের জন্যে। কিন্তু খ্রিস্টানরা নিজেরাই শরীয়তের বিধি লংঘন করেছে এবং তওরাতে তাদের প্রতি যা যা হারাম করা হয়েছিল সে সবকেই তারা হালাল বানিয়ে নিয়েছে। খাদ্য-পানীর ব্যাপারে তারা পবিত্র ‘পোলস’- এর বিধি বিধান পালন করে এবং দেবতা মূর্তির জন্যে উৎসর্গীকৃত জন্তু ছাড়া আর সব কিছুকেই তারা হালাল ঘোষণা করল। পোলস্ তার কারণ দর্শিয়ে বলেছে, ‘পবিত্র লোকদের জন্য সব কিছুই পবিত্র। আর যা কিছুই মুখের মধ্যে চলে যায়, তা অপবিত্র করে না। বরং যা মুখ থেকে নির্গত হয়, তাই নাপাক করে দেয়।’ এ যুক্তির ভিত্তিতেই তারা শূকরের গোশ্তও জায়েয করে নিল অথচ তওরাতে কিতাবের সুস্পষ্ট ঘোষণুযায়ী তা আজ পর্যন্ত তাদের জন্যে সম্পূর্ণ হারাম হয়ে রয়েছে।
ইসলাম পূর্ব যুগের আরবদের অবস্থা
ইসলামের আগমণের পূর্বে জাহিলিয়াতের যুগে আরব সমাজ কোন কোন জন্তুকে নাপাক মনে করে এবং কোন কোনটিকে দেবদেবীর নৈকট্য লাভ ও কুসংস্কার অনুসরণের দরুন নিজেদের জন্যে হারাম করে নিয়েছিল। বহীরা, সায়েবা, অসীলা ও হাম প্রভৃতি এ পর্যায়ে হারাম জন্তু-পূর্বে এর ব্যাখ্যঅ দেয়া হয়েছে। আর তার বিপরীত মৃত জীব এ বহমান রক্ত প্রভৃতি অনেক নাপাক জিনিসই জায়েয ও হালাল ঘোষণা করেছিল।
ইসলাম পবিত্র জিনিসগুলো মুবাহ করেছে
ইসলাম আগমনকালে আরব দেশের লোকেরা পাশব খাদ্যের ব্যাপারে পূর্ববর্তিরূপে নানাভাবে বিপরীত চিন্তায় জর্জরিত ছিল। এ কারণে সমগ্র মানুষকে সম্বোধন করে ইসলাম বলেছেঃ
يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ
হে জনগণ, জমিনে যে সব জিনিস হালাল পবিত্র তা ভক্ষণ কর এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ কর না। কেননা শয়তান তোমাদের জন্যে প্রকাশ্য শত্রু। (সূরা বাকারাঃ ১৬৮)
অন্য কথায়, ইসলাম সর্বসাধাণেকে নির্বিশেষে আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, ‘হে লোকেরা তোমরা পৃথিবীর এ বিশাল-বিস্তীর্ণ দস্তুরখানা থেকে পবিত্র উৎকৃষ্ট জিনিসগুলো খাদ্য হিসেবে গ্রহণ কর। আর শয়তানের দেখানে পথে আদৌ চলবে না’। অর্থাৎ আল্লাহ যা হালাল করেছেন, তাকে হারাম গণ্য করে বিভ্রান্তির গভীর গহ্বরে নিপতিত হবে না। অতঃপর মুমিনদের প্রতি বিশেষভাবে সম্বোধন করে বলা হয়েছেঃ
.................. আরবী ...............
হে ঈমানদার লোকেরা! আমরা তোমাদেরকে যেসব পবিত্র জিনিস রিযিক স্বরূপ দিয়েছি তোমরা তা খাও ও আল্লাহ্র শোকর কর যদি তোমরা বিশেষ ও একান্তভাবে তাঁরই বন্দেগী করতে প্রস্তুত হয়ে থাক। তিনি তো তোমাদের জন্যে শুধু মৃত বস্তু, রক্ত ও শূকরের গোশ্ত এবং আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো নামে জবেহ দেয়া জন্তু হারাম করে দিয়েছেন। তবে যে কেউ চরমভাবে ঠেকায় পড়ে যায়- কিন্তু সে তার জন্যে ইচ্ছুকও নয়, তার পক্ষে তা ভক্ষণ করায় কোন গুনাহ হবে না। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়াবান।
এই বিশেষভাবে সম্বোধন করে বলা কথার দ্বারা আল্লাহ্ ঈমানদার লোকদের নির্দেশ দিয়েছেন যে, তারা যেন পবিত্র উৎকৃষ্ট আহার করে। সেই সঙ্গে দয়াবান দাতার যেন তারা শোকর আদায় করে, তাঁর নিয়ামতের দানসমূহের মর্যাদা রক্ষা করে হক্ আদায় করে। তারপর বলা হয়েছে, আয়াতটিতে যে চার ধরণের জিনিসের উল্লেখ করা হয়েছে, সে কয়টি ছাড়া অন্য কোন জিনিসই আল্লাহ্ হারাম করেন নি। বলা হয়েছেঃ
قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
বল, আমার প্রতি যে ওহী নাযিল হয়েছে তাতে তো কোন আহারকারীর প্রতি কোন জিনিস হারাম বলে চিহ্নিত হতে দেখি না- মৃত জন্তু, প্রবাহিত রক্ত ও শূকরের গোশত অথবা আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য কারোর উদ্দেশ্যে বলি দেয়া জন্তু ব্যতীত। কেউ যদি ঠেকায় পড়ে এসব থেকে কিছু আহার করে- আগ্রহী ইচ্ছুক বা প্রয়োজনের সীমালংঘনকারী না হয়ে তাহলে তোমার আল্লাহ্ নিশ্চয়ই ক্ষমাশীল দয়াবান। (সূরা আন’আমঃ ১৪৫)
সূরা আল-মায়িদায় এসব হারাম জিনিসের বিবরণ পেশ করার পর বলা হয়েছেঃ
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ
তোমাদের প্রতি মৃত জীব, রক্ত, শূকরের মাংস, যা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য দেবদেবীর জন্যে উৎসর্গীকৃত হয়েছে, যা গলায় ফাঁস লেগে মরেছে, যা আঘাত পেয়ে মরেছে, যা উপর থেকে পড়ে গিয়ে মরেছে, যা শিং-এর গুতা খেয়ে মরেছে, যা কোন হিংস্র জন্তু কর্তৃক ছিন্ন ভিন্ন হয়েছে, যা তোমরা যবেহ করতে পেরেছ তা ব্যতীত আর যা কোন দেবীর উদ্দেশ্যে বলি দেয়া হয়েছে। (সূরা আল মায়েদাঃ ৩)
এ আয়াতে দশটি হারাম জন্তুর উল্লেখ করা হয়েছে। তার পূর্ববর্তী আয়াতে মাত্র পাঁচটি হারাম জিনিসের উল্লেখ ছিল। তাই এ দুয়ের মাঝে কোন বৈপরীত্য নেই। বরং একটি আয়াত অপর আয়াতের ব্যাখ্যা বিশেষ। কেননা গলায় ফাঁস লেগে, আঘাত পেয়ে, ওপর থেকে পড়ে গিয়ে, শিং- এর গুতায় হিংস্র জন্তু কর্তৃক ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে মৃত- এ সব জন্তুই আসলে মৃত, মৃতেরই বিভিন্ন রূপ মাত্র। দেবীর উদ্দেশ্যে বলি দেয়া জন্তুও অ-আল্লাহ্র নামে যবেহ করা জন্তুর পর্যায়ে গণ্য। ফলে প্রকৃত পক্ষে চার প্রকারের জন্তুই হারাম।
মৃত জন্তুর হারাম হওয়ার কারণসমূহ
কুরআনের যেসব আয়াতে হারাম খাদ্যসমূহ উল্লেখ রয়েছে তন্মধ্যে সর্বত্র প্রথম উল্লেখিত হয়েছে আল-মায়তা-তা’র। অর্থাৎ সে জন্তু ও পাখি যা স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেছে। অন্য কথায় যে জীব বা পাখির মৃত্যু যবেহ বা শিকার করার ফলে সঙ্ঘটিত হয়নি।
কিন্তু এ জন্তু খদ্য হিসেবে ব্যবহার করতে নিষেধ ও হারাম করার এবং সেটিকে নিষ্ফল ও বিনষ্ট হতে দেয়ার মূলে কি কারণ থাকতে পারে, এ হচ্ছে আধুনিক মন মানসের জিজ্ঞাস্য। উত্তরে বলতে চাই, মৃত জন্তু ও পাখি হারাম হওয়ার ও তাকে বিনষ্ট হয়ে যেতে দেয়ার মূলে কতগুলো কল্যাণমূলক কারণ নিহিত রয়েছেঃ
ক. সুস্থ মানব প্রকৃতি মৃত জীব ঘৃণা করে। বিবেকবান মানুষ মুর্দার খাওয়াকে অত্যন্ত ঘৃণ্য কাজ বলে মনে করে। তা মানুষের জন্যে নিতান্তই অশোভন ও হীন কাজ বলে বিশ্বাস করে। এ কারণেই সমস্ত আসমানী গ্রন্থে ও ধর্মে মুর্দার খাওয়াকে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে ও সর্বত্র জবেহ করা জন্তু খাওয়াকে পছন্দ করা হয়েছে। যবেহ করার পদ্ধতি ও নিয়ম যতই বিভিন্ন হোক না কেন।
খ. মানুষ যা লাভ করার ইচ্ছা করেনি, মনে কামনাও জাগেনি, তা সে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করুক, সেটা আল্লাহ্র পছন্দ নয়। মুর্দারের অবস্থা ঠিক তেমনই। তবে যে জন্তু যবেহ করা হয় কিংবা যা শিকার করা হয়, তাতে মানুষের সংকল্প ও চেষ্টা-যত্নের কোন অংশ শামিল থাকে বলে তা পছন্দনীয় হয়ে থাকে।
গ. যে জন্তু স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেছে, তার সম্পর্কে আশংকা থাকে, হতে পারে সেটি চিরন্তন রোগাক্রান্ত বা কোন দুর্ঘটনার শিকার হয়ে কিংবা বিষাক্ত ঘাস বা উদ্ভিদ খেয়ে মরেছে। আর তাহলে তা খাওয়ার দরুন বিরাট ক্ষতি হওয়ার আশংকা রয়েছে। অথবা হতে পারে তা খুব বেশি দুর্বল বা স্বাস্থ্য খারাপ হওয়ার দরুন সেটি মরেছে।
ঘ. মানুষের জন্যে মুর্দার হারাম করে আল্লাহ তা’আলা পশু-পাখিগুলোর জন্য বিশেষ রহমতে খাদ্যের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। কেননা সেগুলোও আমাদের ন্যায় আল্লাহ্র সৃষ্টি।
ঙ. আরও একটি দিক হলো এই যে, মানুষ তার মালিকানাধীন জন্তুগুলোকে রোগাক্রান্ত বা দুর্বল হয়ে ধ্বংস হয়ে যাবার জন্যে ফেলে না রাখে। বরং হয় চিকিৎসা করাবে অবিলম্বে কিংবা যবেহ করে চিরশান্তি দান করবে।
প্রবাহিত রক্ত হারাম কেন
হারাম জিনিসগুলোর তালিকায় দ্বিতীয় স্থান হচ্ছে প্রবাহিত রক্তের। হযরত ইবনে আব্বাস রা. এর কাছে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, তিল্লী (প্লীহা) সম্পর্কে শরীয়তের হুকুম কি? তিনি বললেনঃ খেতে পার। লোকেরা বলল, তা তো আসলে জমাট বাধা রক্ত মাত্র? জবাবে বললেন, আল্লাহ্ তা’আলা মাত্র প্রবাহিত রক্ত হারাম করেছেন। কেননা তা অপবিত্র ময়লাযুক্ত, ন্যাক্কারজনক (Filth)। পরিচ্ছন্ন ও পরিশুদ্ধ ও সুস্থ মানব প্রকৃতি তা ঘৃণা না করে পারে না। তাছাড়া মৃত জন্তুর ন্যায় তাতেও ক্ষতিকর জীবাণু থাকা খুবই সম্ভব।
জাহিলিয়াতের যুগে কারো তীব্র ক্ষুধা অনুভূত হলে অস্থি বা কোন ধারাল জিনিস উষ্ট্র কিংবা অন্য জন্তুর গাত্রে বসিয়ে দিত। তাতে যে রক্ত ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে পড়ত, সে তা সাগ্রহে পান করত। এ ধরণের কাজের ফলে জন্তুগুলো মর্মান্তিক জ্বালা-যন্ত্রণা ভোগ করতে বাধ্য হতো। রক্ত বের হয়ে যাওয়ার ফলে সেটার দুর্বল হয়ে পড়া অবশ্যম্ভাবী হয়ে দেখা দিত। এ সব কারণে আল্লাহ্ তা’আলা প্রবহমান রক্ত হারাম করে দিয়েছেন।
শূকরের গোশত
এ তালিকার তৃতীয় জিনিস হচ্ছে শূকরের গোশত। সুস্থ স্বভাব-প্রকৃতি মাত্রই তা ঘৃণা করে। কেননা তা না-পাক। শূকরের গোশতের প্রতি সুস্থ রুচি কোন মানুষ আকর্ষণ বোধ করতে পারে বলে কল্পনাও করা যায় না। কেননা শূকরের অতি লোভনীয় খাদ্য হয় সব রকমের পায়খানা ও ময়লা-আবর্জনা। আধুনিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের দৃষ্টিতেও তা খাওয়া সর্বত্রই বিশেষ করে, গ্রীষ্ম প্রধান দেশে খুবই ক্ষতিকর। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষণ থেকেও প্রমাণিত হয়েছে যে, শূকরের গোশত আহার করা হলে দেহে এমন এক প্রকারের পোকার সৃষ্টি হয়, যা স্বাস্থ্যকে কুরে কুরে খায়।
{বিজ্ঞানের সর্বশেষ পরীক্ষণে জানা গেছে, শূকর গোশতে এসব জীবাণু জন্মিতে পারেঃ Cysticerus teunicallis, Cysticereus cellulosae Spargamune mousoni, Echinococeus podymorphus, paragonimus weater manall- অনুবাদক}
ভবিষ্যতে তার ক্ষতির আরও অনেক দিক- অনেক কারণ- আবিষ্কৃত হতে পারে। অনেক বিশেষজ্ঞের মতে শূকরের গোশত সব সময় আহার করলে মানব চরিত্রে নির্লজ্জতা জাগে, আত্মমর্যাদা বোধ শেষ হয়ে যায়।
আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্যে উৎসর্গিত জন্তু
চতুর্থ হারাম জন্তু হচ্ছে আল্লাহ্ ছাড়া কারো জন্যে উৎসর্গীকৃত জন্তু-জানোয়ার ভক্ষণ করা। তাও হারাম। অর্থাৎ আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো নামে কোন জন্তু যবাই বা বলি দেয়া হলে, তাতে অপর কারো নাম উচ্চারণ করা হলে তা মুসলমান মাত্রের জন্যেই হারাম হয়ে যায়। মূর্তিপূজারীরা তাদের দেবদেবী ও প্রতিমার জন্যে জন্তু-জানোয়ার উৎসর্গ করত বা এখনও করছে। বলি দিত বা যবেহ করত। যেহেতু তা এক আল্লাহ্ ছাড়া দেবদেবীদের জন্যে উৎসর্গীকৃত হয়েছে এবং তা করে সে সবের নৈকট্যলাভ করতে চাওয়া হয়েছে, তার বন্দেগী করতে চাওয়া হয়েছে এবং তা চরম শির্ক- এর কাজ। এ কারণে এক আল্লাহর প্রতি ঈমানদার মানুষ সে সব জন্তু খেতে পারে না। তওহীদী দ্বীনের দৃষ্টিতে তা খাওয়া পরিষ্কার শির্ক। এ কারণেই তা হারাম। তওহীদী আকীদা-বিশ্বাসের পরিবত্রতা সংরক্ষণ এবং শিরক ও বতু-পরস্থি থেকে মানুষকে দূরে রাখা, তার প্রতি মানুষকে বিক্ষুব্ধ করে তোলাই এর উদ্দেশ্য।
আল্লাহ তা’আলাই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। তার জন্যে পৃথিবীর সব কিছু নিয়ন্ত্রিত করেছেন। জন্তু-জানোয়ারও মানুষের অধীন, মানুষের খিদমতে নিয়োজিত। মানুষের কল্যাণের জন্যে তা যবেহ করা সম্পূর্ণ জায়েয। তবে শর্ত এই যে, যবেহ করার সময় এক আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করতে হবে, বলতে হবেঃ ‘আল্লাহু আকবর’। তাহলে তা থেকে প্রমাণিত হবে যে, একটি জীবন্ত সৃষ্টিকে যবেহ করে তার প্রাণ সংহার করার এই কাজটি করা হচ্ছে সেই আল্লাহ্রই দেয়া অনুমতিক্রমে। কিন্তু যবেহ করার সময় অন্য কারো নাম উচ্চারিত হলে আল্লাহ্র এই অনুমতিকে কার্যত নাকচ করে দেয়া হয়। এ কারণে এই জন্তুটিকে হারাম ঘোষণা করে তা থেকে লোকটিকে দূরে রাখতে চাওয়া হয়েছে।
কয়েক প্রকারের মুর্দার
মোটামুটি এই চারটি জিনিসই মূলত হারাম। তবে সূরা আল-মায়িদায় তার যে কিছুটা বিস্তারিত বিবরণ এসেছে, সে দৃষ্টিতে তার সংখ্যা দশ হয়ে যায়। অবশিষ্টগুলো এইঃ
৫. মুনখানিকাতুঃ গলায় ফাঁস লেগে মরা জন্তু;
৬. মওকুয়াতুঃ লাঠি বা অন্য কোন শক্ত জিনিসের আঘাতে মরে যাওয়া জন্তু;
৭. মুতারাদ্দিয়াতুঃ উচ্চস্থান থেকে পড়ে গিয়ে বা কূয়া কিংবা খালে পড়ে মরে যাওয়া জন্তু;
৮. নতীহাতুঃ অপর কোন জন্তুর শিং-এর গুঁতায় মরে যাওয়া জন্তু;
৯. হিংস্র জন্তু কর্তৃক ছিন্নভিন্ন হয়ে যাওয়া জন্তু- যার দেহের কোন অংশ খেয়ে ফেলেছে, আর এ কারণে তার মৃত্যু ঘটেছে; এই পাঁচ প্রকারের জন্তুর উল্লেখ করার পর আল্লাহ্ তা’আলা ইরশাদ করেছেন- এই সবের মধ্য থেকে কোন জন্তুকে জীবিত পেয়ে সেটিকে যবেহ করা হলে তা হারাম নয়; বরং তা তোমরা খেতে পার। যবেহ করার জন্যে জীবনের ধুঁকধুঁকি থাকাই যথেষ্ট। হযরত আলী রা. বলেছেনঃ
.......... (আরবী)....................
লাঠির আঘাতে, উপর থেকে পড়ে, শিং-এর গুঁতোয় মরে যাওয়া এসব জন্তুকে জীবিত থাকা অবস্থায়- যখন হাত বা পা নাড়ায়-যবেহ করা হলে তা তোমরা খাবে।
‘দাহ্হাক’ বলেছেনঃ জাহিলিয়াত যুগের লোকেরা এসব জন্তু যবেহ না করেই ভক্ষণ করত। কিন্তু আল্লাহ্ তা’আলা ইসলামে এসব খাওয়াকে হারাম করে দিয়েছেন। তবে এর মধ্য থেকে যেটির সামান্য আয়ু থাকতেও- পা, লেজ বা চক্ষু নড়াচড়া করা অবস্থায় যবেহ করা গেলে তা হালাল হবে।
(কোন কোন ফিকাহ্বিদের মতে তার মধ্যে জীবনের স্থিতি থাকা আবশ্যক। যা রক্ত প্রবাহিত হওয়া ও হাত-পা শক্তভাবে নড়াচড়া করতে থাকলে তবে যবেহ করার পর হালাল হবে।)
এসব মুর্দার হারাম করার কারণ
এসব মুর্দার হারাম হওয়ার মূলে সেসব কারণ ও উদ্দেশ্যই নিহিত রয়েছে যা ইতিপূর্বে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। বিশেষভাবে বলা চলে, মানুষ জন্তু-জানোয়ারের প্রতি দয়াশীল এবং ওসবের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব সম্পর্কে পূর্ণ অনুকম্পা সম্পন্ন হয়ে উঠুক- শরীয়তের এটাই লক্ষ্য। মানুষ যেন জন্তুগুলোকে অসহায় করে ছেড়ে না দেয়। এ রকম যে, কোনটি গলায় ফাঁস লাগিয়ে মরল, আর কোনটি উঁচুস্থান থেকে পড়ে গিয়ে মরল, আর কোনটি অন্য জন্তুর সাথে লড়াইয়ে লিপ্ত হয়ে শিং-এর গুঁতা খেয়ে মরে গেল, জন্তুর মালিক সে ব্যাপারে নিজের কোন দায়িত্বই অনুভব করে না, তা আল্লাহ্র আদৌ পছন্দ নয়। জন্তুগুলোকে কেউ এমন নির্মমভাবে মারধোর করে, যার ফলে সেটির মরে যাওয়া অবধারিত হয়ে পড়ে। তা আল্লাহ্র অসন্তুষ্টির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। জন্তুর লড়াই লাগিয়ে অনেকে আনন্দ পায় বা জয়-পরাজয় নির্ধারণ করে। তাতে একটি জন্তু অপর জন্তুটিকে গুঁতিয়ে আহত ও রক্তরঞ্চিত করে দেয় এবং তার ফলে সেটির মরে যাওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। এই কাজও আল্লাহ পছন্দ করেন না।
হিংস্র জন্তুর ছিন্নভিন্ন করে দেয়া পশু খাওয়াও হারাম। তাতে মানুষের মর্যাদা রক্ষাই আসল লক্ষ্য। কেননা, পশুর উচ্ছিষ্ট খাওয়া মানুষের জন্যে শোভন হতে পারে না। তা থেকে মানুষকে দূরে রাখতে চাওয়া হয়েছে। জাহিলিয়াত যুগে এসব জন্তুকে লোকেরা নিঃসংকোচে খেত। কিন্তু আল্লাহ্ তা’আলা হিংস্র জন্তুর উচ্ছিষ্ট খাওয়া মুমিনদের জন্যে হারাম করে দিয়েছেন।
দেবতার উদ্দেশ্যে বলি দেয়া জন্তু
হারাম জন্তুগুলোর মধ্যে দশম হচ্ছে সেই জন্তু, যা কোন দেবতার উদ্দেশ্যে বলিদানের জন্যে নির্দিষ্ট স্থানে হত্যা করা হবে। যার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হবে আল্লাহ্ ছাড়া অপর কোন শক্তি, ব্যক্তি বা দেবতার পূজা করা। জাহিলিয়াত যুগে কাবা ঘরের চতুর্দিকে এ রকমের অনেক ‘স্থান’ নির্মিত হয়েছিল। আর তখনকার লোকেরা তাদের উপাস্য দেবতাদের পূজা করা ও সে সবের নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে সেসব স্থানে পশু যবাই করত। এক কথায় এটাও অ-আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে বলিদান মাত্র। উভয় ক্ষেত্রেই অ-আল্লাহ্ শক্তির প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা জানানো ও তা বড় করে তোলা- তার বড়ত্ব দেখানোই চরম লক্ষ্য। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, ‘অ-আল্লাহ্র নামে যবেহ করা জন্তু’ কথাটি সে জন্তুর জন্যে ব্যবহৃত হতে পারে যেটিকে যবেহ করার সময় কোন ‘বুত’ সম্মুখে নেই। বরং কোন বুতের নামে যবেহ করা হলেই হলো। কিন্তু স্থান- এ যবেহ করা জন্তু আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো নামে যবেহ না করা হলেও তা হারাম হবে। অন্য কথায় প্রথমাবস্থায় ‘স্থান’ নির্দিষ্ট থাকে না। আর দ্বিতীয় অবস্থায় স্থান সুনির্দিষ্ট থাকে।
কাবাঘরের চতুর্দিকে যেসব ‘স্থান’ নির্মিত হয়েছিল, লোকদের ধারণা ছিল, এসব স্থানে জন্তু যবেহ করা হলে তাতে আল্লাহ্র ঘরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হবে। কুরআন এই ভুল ধারণার অপনোদন করেছে এবং এই কাজটিকে সুস্পষ্টভাবে হারাম ঘোষণা করেছে। নতুবা অ-আল্লাহ্র জন্যে যবেহ করা জন্তু বলতে ‘স্থান’-এ যবেহ করা জন্তুটিও শামিল রয়েছে।
মাছ ও পঙ্গপাল সম্পর্কে স্বতন্ত্র বিধান
ইসলামে মাছ ও এ ধরণের জলজ জন্তু সম্পর্কে স্বতন্ত্র বিধান দেয়া হয়েছে। তাকে হারাম করা জন্তুগুলোর মধ্যে গণ্য করা হয়নি। নবী করীম সা. সমুদ্র-পানি সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হলে তিনি জবাবে ইরশাদ করলেনঃ
........... আরবী ...............
সমুদ্রের পানি পবিত্র এবং তার মুর্দার হালাল।
কুরআন মজীদে বলা হয়েছেঃ
........... আরবী ...............
সমুদ্রের শিকার এবং তার খাদ্য তোমাদের জন্যে হালাল করা হয়েছে।
হযরত উমর রা. এ আয়াতাংশের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেছেনঃ
‘সমুদ্রের শিকার’ বলতে সমুদ্রে যা কিছু শিকার করা হয় সে সব জীব বোঝান হয়েছে। আর সমুদ্রের খাদ্য বলতে বুঝিয়েছে তা যা সমুদ্র নিজেই ওপরে নিক্ষেপ করে।
হযরত ইবনে আব্বাস রা. ও বলেছেনঃ সমুদ্রের খাদ্য বলতে সমুদ্রের ‘মৃত জীব’ বুঝান হয়েছে।
বুখারী ও মুসলিম গ্রন্থে হযরত জাবির রা. থেকে বর্ণিত এই হাদীস খানি উদ্ধৃত হয়েছেঃ
........... আরবী ...............
নবী করীম সা. সাহাবীদের একটি বাহিনীকে কোন বিশেষ অভিযানে প্রেরণ করেন। তাদের হাতে একটি বড় মাছ পড়ে। সমুদ্র মাছটিকে ওপরে নিক্ষেপ করেছিল অর্থাৎ সেটি ছিল মৃত। তারা মাছটিকে বিশ দিনেরও বেশি সময় ধরে আহার করতে থাকেন। পরে তাঁরা মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলেন, তখন তাঁরা নবী করীম সা. কে এ বিষয়ে অবহিত করলেন। তিনি তাঁদের বললেনঃ ‘আল্লাহ্ তোমাদের জন্যে যে রিয্ক বের করেছেন, তোমরা তা খাও। সে মাছটির কোন অংশ তোমাদের কাছে অবশিষ্ট থাকলে তা আমাদেরও খাওয়াও।’ তখন কেউ কেউ সে মাছের কিছু অংশ নবী করীম সা. এর খেদমতে পেশ করেন। তিনি তা আহার করেন। (বুখারী)
পঙ্গপাল সম্পর্কেও শরীয়তের এই বিধানই কার্যকর। নবী করীম সা. মৃত পঙ্গপাল আহার করার অনুমতি দিয়েছেন। কেননা তা যবেহ করা যায় না। হযরত ইবনে আবু লাইলা বলেছেনঃ
........... আরবী ...............
আমরা রাসূলে করীম সা. এর সঙ্গে সাতটি যুদ্ধাভিযানে গিয়েছি। আর তখন তাঁর সঙ্গে আমরা পঙ্গপাল আহার করেছি।
মৃত জন্তুর চামড়া, অস্থি ও পশম ব্যবহার
‘মুর্দার হারাম’ অর্থ তা খাওয়া হারাম। কিন্তু মৃত জন্তুর চামড়া, শিং, অস্থি ও পশম ব্যবহার করায় কোন দোষ নেই। শুধু তাই নয়, তা কাম্যও বটে। কেননা তা এমন সম্পদ যা ব্যবহার করা ও কাজে লাগানো সম্ভব। অতএব বিনষ্ট করা জায়েয হতে পারে না।
হযরত ইবনে আব্বাস রা. বলেছেনঃ
উম্মুল মু’মিনীন হযরত মায়মুনার ক্রীতদাস দানস্বরূপ একটা ছাগল লাভ করে। পরে সেটি মরে যায়। নবী করীম সা. তা দেখতে পেয়ে বললেনঃ তোমরা এটির চামড়া তুলে নিচ্ছ না কেন, তা পরিচ্ছন্ন ও পরিপক্ক করে তোমরা কাজে লাগাবে। লোকেরা বলল, ওটা তো মরে গেছে। রাসূল সা. বললেনঃ মুর্দার খাওয়াটাই শুধু হারাম।
নবী করীম সা. মৃত জন্তুর চামড়া পবিত্র পরিচ্ছন্ন করার নিয়ম জানিয়ে দিয়েছেন। বলেছেনঃ
........... আরবী ...............
চামড়া দাবাগাত করে পবিত্র-পরিচ্ছন্ন করা জন্তুটিকে যবেহ করার শামিল। (আবু দাউদ, নিসায়ী)
অপর একটি বর্ণনায় উদ্ধৃত হয়েছেঃ
‘দাবাগাত’ চামড়ার ময়লা অপবিত্রতাকে দূর করে দেয়। (হাকেম)
‘মুসলিম প্রভৃতি গ্রন্থে নবী কারীম সা. এর এ উক্তিটি উদ্ধৃত হয়েছেঃ
........... আরবী ................
যে চামড়াই ‘দাবাগাত’ (Tanning) করা হবে সেটিই পবিত্র হয়ে যাবে।
এ এক সাধারণ বিধান। সকল প্রকার জন্তুর চামড়া সম্পর্কেই এ বিধান প্রযোজ্য। কুকুর ও শূকরের চামড়ার ব্যাপারও ভিন্নতর কিছু নয়। ফিকাহবিদদের এই মত।
উম্মুল মুমিনীন হযরত সওদা রা. বলেছেনঃ
আমাদের একটি ছাগল মরে গেল। তখন আমরা তার চামড়া দাবাগাত করে নিই। পরে আমরা সব সময় তাতে ‘নবীয’ (খেজুরের শরবত) তৈরী করতে থাকি। এভাবে সেটি আমাদের একটি পুরাতন মশক পাত্রে পরিণত হয়ে গেল। (বুখারী)
ঠেকার অবস্থায় স্বতন্ত্র হুকুম
এখানে যে হারামের বিধান ব্যাখ্যা করা হচ্ছে, আসলে তা সুস্থ ও শান্তিপূর্ণ অবস্থায় স্বাধীন ইচ্ছায় গ্রহণীয় নীতি। কিন্তু ঠেকার অবস্থা তা থেকে স্বতন্ত্র। পূর্বে এ পর্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। আল্লাহ্ বলেছেনঃ
وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ
আল্লাহ্ তা’আলা ভিন্ন ভিন্ন করে তোমাদের বলে দিয়েছেন, যা কিছু তোমাদের জন্যে হারাম করেছেন। তবে ব্যতিক্রম রয়েছে যদি তোমরা ঠেকায় পড়ে গিয়ে তার কোনটি গ্রহণ করতে বাধ্য হও। (সূরা আন’আমঃ ১১৯)
‘ঠেকায় পরে গ্রহণ করতে বাধ্য হওয়া’ একটা সর্ববাদী সম্মত ও সমর্থিত ব্যাপার। খাদ্যের পর্যায়ে এই ‘ঠেকায় পড়াটা’ কে অনেক সময় লক্ষ্য করা যায়। যেমন কেউ ক্ষুধায় খুব বেশি কাতর হয়ে পড়ল। (কোন কোন ফিকাহ্বিদের মতে) এই ক্ষুধার্তবস্থায় তার একটি দিন ও একটি রাত অতিবাহিত হয়ে গেল। কিন্তু এ সময়ের মধ্যে সে এমন কিছু পেল না, যা খেয়ে সে তার ক্ষুধা নিবৃত্ত করতে পারে। এ সময় তার সম্মুখে সহজলভ্য হয়ে আছে শুধু হারাম খাদ্য। তখন সে ন্যূনতম পরিমাণ গ্রহণ করে প্রয়োজন পূরণ করতে পারে ও নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভ করতে সক্ষম হতে পারে। শরীয়তে তার জন্যে এ অনুমতি রয়েছে। ইমাম মালিক র. বলেছেনঃ
............ আরবী ............
ঠেকায় পড়ে হারাম খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ হচ্ছে পেট পূর্ণ হওয়া (Satisfaction) এবং হালাল খাদ্য পাওয়ার সময় পর্যন্ত তা থেকে পাথেয় গ্রহণ।
কিন্তু অন্যান্যরা বলেছেনঃ
............ আরবী ............
এ ঠেকায় পড়া লোকটি শুধু এতটা পরিমাণ হারাম খাদ্য গ্রহণ করতে পারে, যতটা শেষ শ্বাস-প্রশ্বাসটা চলমান রাখার জন্যে যথেষ্ট হতে পারে।
সম্ভবতঃ এ মতটিই কুরআনের ঘোষণার- (আরবী) ‘অধিক ইচ্ছুক-আগ্রহী ও সীমালংঘনকারী না হয়ে’- সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ক্ষুধার ব্যাপারটিকে সুস্পষ্ট করে দেয়ার জন্যে কুরআনে সুস্পষ্ট করে বলা হয়েছেঃ
............ আরবী ............
যে লোক ক্ষুধার তাড়নায় বাধ্য হয় কোন হারাম জিনিস খায়, গুনাহর প্রতি কোনরূপ প্রবণতা ও আগ্রহ ব্যতীতই, তাহলে আল্লাহ্ নিশ্চয়ই ক্ষমাশীল ও দয়াবান।
চিকিৎসার প্রয়োজনে
চিকিৎসা পর্যায়ে ঠেকে যাওয়ার রূপটি হচ্ছে, কোন হারাম জিনিস ঔষধ হিসেবে গ্রহণ করার ওপরই যদি কারো রোগমুক্তি নির্ভরশীল হয়ে পড়ে, তাহলে এ সম্পর্কে শরীয়তের হুকুম কি হবে তাই প্রশ্ন। ফিকাহবিদগণ এ বিষয়ে বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। কোন কোন ফিকাহ্বিদ চিকিৎসার ব্যাপারটিকে খাদ্যের মতো অতটা তীব্র কঠিন অনিবার্য প্রয়োজনীয় বলে মনে করেন না। এ মতের সমর্থনে তাঁরা রাসূলে কারীম সা. এর একটি বাণীরও উল্লেখ করেছেন। হাদীসটি হচ্ছেঃ
............ আরবী ............
তোমাদের প্রতি যা যা হারাম করা হয়েছে, তাতে আল্লাহ্ তোমাদের রোগমুক্তির ব্যবস্থা রাখেন নি। (বুখারী)
অনেক ফিকাহ্বিদ আবার চিকিৎসার প্রয়োজনটিকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করেছেন এবং ওষুধ বা চিকিৎসার ব্যাপারটিকেও খাদ্যের সমান প্রয়োজনীয় বলে মনে করেছেন। কেননা মূলত জীবনের জন্যে যেমন খাদ্য প্রয়োজনীয়, তেমনি ঔষধের প্রয়োজনও কোন ক্রমেই অস্বীকার করা যায় না। তাই এ নিষিদ্ধ দ্রব্যাদি প্রয়োজনে ঔষধ হিসেবে ব্যবহার করা তাঁদের মতে নিশ্চয়ই মুবাহ হওয়া বাঞ্ছনীয়। দলিল হিসেবে তাঁরা আরও বলেছেন, হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ ও জুবাইর ইবনুর আওয়াম রা. চর্ম রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। নবী করীম সা. তাঁদের জন্যে রেশমী পোশাক ব্যবহার করার অনুমতি দিয়েছিলেন- যদিও তা সাধারণভাবে নিষিদ্ধই ছিল এবং তা পরার ওপর নবী করীম সা. অভিশাপ বর্ষণ করেছেণ।
সম্ভবতঃ এ মতটিই ইসলামের মৌল ভাবধারার সাথে সামঞ্জস্যশীল। কেননা মানুষের জীবন রক্ষার জন্যে যে-কোন কার্যকর পন্থা গ্রহণ প্রতিটি শরীয়তী ব্যবস্থারই মূল লক্ষ্য।
কিন্তু হারাম দ্রব্য সম্বলিত ঔষধ চিকিৎসার্থে ব্যবহার করার অনুমতি কতিপয় শর্তের ওপর ভিত্তিশীল। শর্তগুলো হচ্ছেঃ
১. সে ঔষধটি ব্যবহার করা না হলে স্বাস্থ্যের ওপর প্রকৃতই কোন বিপদ ঘনিয়ে আসতে পারে বলে নিশ্চিতভাবে বিবেচিত হতে হবে।
২. সে ঔষধটি ছাড়া তার স্থলাভিষিক্ত বা বিকল্প হতে পারে হালাল দ্রব্য সম্বলিত এমন কোন ঔষধ পাওয়াই যায় না- এমন অবস্থা হতে হবে।
৩. এ বিষয়ে আল্লাহ্ বিশ্বাসী মুসলিম চিকিৎসকের কাছ থেকে সুস্পষ্ট অনুমোদন পেতে হবে।
আমাদের নিজস্ব জ্ঞান তথ্য ও বিশ্বাসযোগ্য চিকিৎসাবিদদের থেকে প্রাপ্ত বর্ণনাসমূহের ভিত্তিতে একটি কথা আমরা অতিরিক্ত বলতে চাই। তা হচ্ছে, কোন হারাম দ্রব্য সম্বলিত ঔষধ ব্যবহার করা জীবন রক্ষার জন্যে একেবারে অপরিহার্য হয়ে দাঁড়াবে, এমন অবস্থা আসলেই নয়। তবু নীতিগতভাবে ও সতর্কতার ভিত্তিতে আমরা এ ধরণের ঔষধ ব্যবহারের অনিবার্যতাকে অস্বীকার করছি না। কেননা কোন মুসলিমের এমন স্থান বা অবস্থায় পড়ে যাওয়া- যেখানে এসব হারাম ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায় না- একেবারে অসম্ভব মনে করা ঠিক নহে।
সামষ্টিক পর্যায়ে প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা থাকলে ব্যক্তি-প্রয়োজন অবশিষ্ট থাকে না
এক ব্যক্তি তার নিজ দেশে খাদ্যবস্তু পায় না বা তার কাছে তা নেই, এটা হতে পারে। কিন্তু তাই বলে সে সব দিক দিয়ে চরম ঠেকায় পড়ে গেছে এবং এখন সে হারাম খাদ্য না খেলে তার প্রাণ বাঁচে না, একথাটি গ্রহণীয় হতে পারে না। কেননা সে যে দেশের নাগরিক ও যে সমাজের একজন, সে দেশ ও সমাজের বা তার লোকজনের কাছে তো বিপুল খাদ্যসম্ভার মজুদই রয়েছে। এরূপ অবস্থায় ঠেকায়-পড়া ব্যক্তির প্রয়োজন পূরণ করতে হবে অন্যান্য লোকের উদ্বৃত্ত খাদ্যসম্ভার থেকে। এরূপ ব্যবস্থার সাহায্যে এ লোকটিকে হারাম খাওয়া থেকে রক্ষা করা যেতে পারে এবং তা একান্তই কর্তব্য। বস্তুত পারস্পরিক সহযোগিতার মধ্যে সে ইসলামী সমাজের পূর্ণত্ব বিধান করতে হবে। এ সমাজের প্রত্যেকে অপর প্রত্যেকের জন্যে দায়ী। এ সমাজের সমস্ত ব্যক্তিসত্তার সমষ্টি এক অভিন্ন ব্যক্তিসত্তায় পরিণত হয়ে থাকে। এ ধরণের সমাজই হতে পারে শিশাঢালা প্রাচীর বিশেষ। তার প্রতিটি ইট খণ্ড অপরাপর ইট খণ্ডসমূহের জন্যে পৃষ্ঠপোষক। (হাদীসের মর্ম)
সামষ্টিক দায়িত্ব পালন পর্যায়ে ইমাম ইবনে হাজম-এর একটি উদ্বৃতি ইসলামের ফিকাহবিদদের জন্যে দিশারী হয়ে আছে। তিনি লিখেছেনঃ
কোন মুসলিম ব্যক্তির জন্যে চরম ঠেকায়-পড়া অবস্থায়ও মুর্দার বা শূকরের মাংস আহার করা কোন ক্রমেই জায়েয হতে পারে না। কেননা তার মুসলিম বা অমুসলিম প্রতিবেশির কাছে অতিরিক্ত খাদ্যবস্তু মজুদ রয়েছে। এমতাবস্থায় তার কর্তব্য হচ্ছে ক্ষুধার্ত ব্যক্তিকে খাবার দেয়া। এ প্রেক্ষিতে ঠেকায়-পড়া লোকটির জন্যে মুর্দার বা শূকরের মাংস খেতে বাধ্য মনে করা যায় না। তার পক্ষে তার প্রতিবেশীর কাছ থেকে খাদ্য-পানীয়ের অতিরিক্ত অংশ হাসিল করা সম্পূর্ণ বৈধ- তার এ অধিকার রয়েছে। এ উদ্দেশ্যে তাকে যদি লড়াইও করতে হয় এবং তাতে সে মৃত্যুও বরণ করে, তাহলে হত্যাকারীর ‘কিসাস’ হতে হবে। আর এ অতিরিক্ত খাদ্য গ্রহণের পথে বাধাদানকারীকে যদি হত্যাও করতে হয় তবু তা করা যাবে এবং নিহত ব্যক্তির ওপর আল্লাহ্র অভিশাপ বর্ষিত হবে। কেননা এ নিহত ব্যক্তি একজন ঠেকায়-পড়া ক্ষুধার্ত ব্যক্তিকে তার বৈধ অধিকার লাভের পথে বাধা দিয়েছে। এ কারণে সে বিদ্রোহী লোকদের মধ্যে গণ্য হবে। আর তার বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্যে আল্লাহ্ তা’আলা নির্দেশ দিয়েছেনঃ
فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ
পরে তাদের একটি পক্ষ যদি অপর পক্ষের ওপর আক্রমণ চালায়, তাহলে এ সীমালংঘনকারীদের ওপর যুদ্ধ চালাও, যেন শেষ পর্যন্ত তারা আল্লাহ্র বিধানের দিকে প্রত্যাবর্তন করে। (সূরা হুজুরাতঃ ৯)
সত্যি কথা, যে ভাইর অধিকার হরণ বা অস্বীকার করা হয় কিংবা তার পথে বাধার সৃষ্টি করে মূলত সে-ই বিদ্রোহী। হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা. এ কারণেই যাকাত দিতে অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন।
যবেহ করার শরীয়তসম্মত পন্থা
সামুদ্রিক জীব সবই হালাল
জীব, জন্তু তাদের অবস্থান ও বসবাস স্থানের দৃষ্টিতে দুটি ভাগে বিভক্ত। হয় তারা সামুদ্রবাসী, না হয় স্থল অধিবাসী।
সামুদ্রিক জীব বলতে বেঝায় যেসব প্রাণী যা পানিতে অবস্থান ও বসবাস করে এবং পানি ভিন্ন যাদের জীবন অকল্পনীয়। শরীয়তের দৃষ্টিতে মূলত তা সবই হালাল, তা যেখানেই পাওয়া যাক না কেন। তা পানির মধ্য থেকে জীবিতই ধরা হোক, কি মৃত মরে উঠুক আর নাই উঠুক। ক্ষুদ্রাকার ও বিরাটকার মাছসমূহ এর মধ্যে পড়ে। আর সামদ্রিক কুকুর কিংবা সামুদ্রিক শূকর বলতে যে জীবগুলোকে বোঝায় তাও এবং এ ধরনের অপরাপর মাছ জাতীয় জীব- সবই হালাল পর্যায়ে গণ্য। তাকে ধরেছে বা মেরেছে কিংবা শিকার করেছে- সে মুসলিম কি কাফির- সে প্রশ্ন এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অবান্তর। বস্তুত সমুদ্রে যা কিছু এবং যত কিছুই রয়েছে তা সব হালাল করে দেয়ে আল্লাহ তা‘য়ালা তাঁর বান্দাদের প্রতি বিশাল পর্যায়ের অনুগ্রহ দান করেছেন। সামুদ্রিক জীবদের মধ্য থেকে বিশেষ কোন শ্রেনীকে হারাম ঘোষণা করা হয়নি এবং তাদের যবেহ করার কোন শর্তও আরোপ করা হয়নি। বরং মানুষকে এক্ষেত্রে অবাধ অনুমতি দেওয়া হয়েছে, সে নিজের কষ্ট ও অভাব লাঘবের জন্য যতটা ইচ্ছা সংগ্রহ করে ব্যবহার করতে পারে। আল্লাহ তা‘য়ালা তাঁর বন্দাদের প্রতি তার বিষেশ অনুগ্রহের কথা প্রকাশ প্রসঙ্গেই ইরশাদ করেছেন :
(আরবী***********)
সেই মহান আল্লাহই নদী-সমুদ্রকে নিয়ন্ত্রিত ও নিয়োজিত করে রেখেছেন, যেন তোমরা তা থেকে তাজা গোশত গ্রহণ করতে পার।
বলেছেন :
(আরবী*******************)
তোমাদের জন্যে সমুদ্রের শিকার ও খাদ্য হালাল করে দেয়া হয়েছে। তা তেমাদের ও পরিভ্রমণকারীদের জন্যে সামগ্রী। (সূরা মায়িদা : ৯৬)
এ দুটি আয়াতে সব সামুদ্রিক জীবকেই সাধারণভাবে ও নির্বিশেষে হালাল করার কথা ঘোষিত হয়েছে।
স্থলভাগের হারাম জীব-জন্তু
স্থলভাগের জীব-জন্তু ও প্রাণীকূলের মধ্যে কেবলমাত্র শূকর মাংস, মৃত, রক্ত এবং অ-আল্লাহর নামে উত্সর্গীকৃত বা যবেহকৃত ছাড়া আর কোনটিকেই হারাম ঘোষনা করা হয়নি। এ পর্যায়ের কথা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে।
কিন্তু কুরআন মজীদেই হালাল-হারাম ঘোষণার কিছু দায়িত্ব আল্লাহ তা’আলা হযরত মুহাম্মদ (সা) এর উপর অর্পন করেছেন। তাঁর দায়িত্ব বর্ণনা পর্যায়ে বলা হযেছে :
(আরবী*******************)
তিনি লোকদের জন্যে পবিত্র উত্কৃষ্ট দ্রব্যাদি হালাল করেন এবং খারাপ পচা-নিকৃষ্ট জিনিসসমূহ হারাম করেছেন। (সূরা আল-আরাফ : ১৫৭)
খবীস’ বলতে বোঝায় তা, যা সাধারণভাবে মানব সমষ্টির সুস্থ রুচিতে জঘন্য মনে হয়- কিছু সংখ্যক লোক যদি তা পছন্দ করেও।
এ পর্যায়েরই একটি হাদীস হচ্ছে :
(আরবী**********************)
নবী করীম (সা) খায়বর যুদ্ধের দিনে গার্হাস্থ্য গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন। (বুখারী)
বুখারী ও মুসলিমে উদ্ধৃত হয়েছে : (আরবী**********************)
নবী করীম (সা) নখরধারী সব হিংস্র জীব এবং সব ছিড়ে খাওয়া পাখির গোশত খেতে নিষেধ করেছেন।
বাঘ, শৃগাল, চিতা ইত্যাদি প্রথম পর্যায়ের জন্তু। আর চিল, শকুণ, বাজ প্রভৃতি নখরধারী পাখিগুলো দ্বিতীয় পর্যায়ের।
হযরত ইবনে আব্বাস (রা) এর মত হচ্ছে, কুরআন মজীদের যে চারটি জীব হারাম বলে উল্লিখিত হয়েছে, তাছাড়া আর কোনটিই হারাম নয়। মনে হচ্ছে, হাদীসে যেসব জন্তুর গোশত খেতে নিষেধ করা হয়েছে তাঁর মতে তা খাওয়া হারাম নয়, মাকরূহ মাত্র। অথবা এও হতে পারে যে, তিনি হয়ত এ হাদীস কয়টি জানতেই পারেন নি।
তিনি বলেছেন : (আরবী************************)
ইসলাম-পূর্ব যুগে লোকেরা অনেক কিছু খেত, আর অনেক কিছু খারাপ মনে করে খেত না। পরে আল্লাহ তার নবীকে পাঠালেন এবং তাঁর কিতাব নাযিল করলেন। তাতে তাঁর হালাল ও হারাম সংক্রান্ত ঘোষণা প্রকাশ করলেন। কাজেই তাতে যা হালাল, তা হালালই আর তাতে যা হারাম তা হারামই। আর যে বিষয়ে নীরবতা অবলম্বন করা হয়েছে, তা সবই নির্দোষ ও মাফ।
অতপর তিনি সূরা আল আনয়াম এর পূর্বোদ্ধৃত ১৪৫ নং আয়াতটি পাঠ করেন। এ আয়াতের আলোকেই হযরত ইবনে আব্বাস (রা) মনে করেন যে, গৃহপালিত গাধার গোশত খাওয়া হালাল। ইমাম মালিক (রা) ও এর মতই গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেছেন, হিংস্র ও ছিন্ন-ভিন্ন করে আহারকারী জন্তুগুলোর গোশত খাওয়া হারাম নয়, বড়জোর মাকরূহ।
তবে এ কথা চুড়ান্ত যে, হারাম জন্তুগুলো যবেহ করলেই তা হালাল হয়ে যাবে, এমন কোন কথা নেই। যবেহ করা হলে চামড়া ট্রেনিং না করেই পবিত্র বিবেচিত হতে পারে মাত্র।
গৃহপালিত জন্তু হালাল হওয়ার জন্যে যবেহ করা শর্ত
যে সব স্থলভাগের জন্তু-জানোয়ার খাওয়া জায়েয, তা দুভাগে বিভক্ত।
কতগুলো জন্তু এমন, যা মানুষের নিয়ন্ত্রনাধীন। উট, গরু, ছাগল, ভেড়া ইত্যাদি ধরনের গৃহপালিত জন্তু এবং হাঁস-মোরগ ইত্যাদি যেসব পাখি গার্হাস্থ পর্যায়ে লালন-পালন করা হয়, তা এক প্রকার। আর অপর প্রকারের জীব হচ্ছে সেসব, যা মানুষের নিয়ন্ত্রনে আসে না বা যেসবের উপর নিয়ন্ত্রণ চালান মানুষের সাধ্যাতীত।
প্রথম প্রকারের জন্তু ও পাখিগুলোর গোশত খাওয়া হলাল। তাবে তার জন্যে শর্ত, হচ্ছে, তাকে শরীয়তের প্রথা অনুযায়ী যবেহ করতে হবে।
শরীয়ত অনুযায়ী যবেহ করা শর্ত
শরীয়ত অনুযায়ী যবেহ করার জরুরী শর্ত হচ্ছে :
১. জন্তু যবেহ বা নহর করতে হবে ধারাল অস্ত্র দ্বারা। যেন রক্ত প্রবাহিত হতে পারে ও রগগুলো যেন ভালভাবে কেটে যায়। সে অস্ত্র পাথরেরও হতে পারে, লৌহ বা কাষ্ট নির্মিতও হতে পারে কিংবা হযরত আদী ইবনে হাতেম তায়ী বলেন:
(আরবী******************)
আমি বললাম, হে রাসূল! আমরা জন্তু শিকার করি, কিন্তু তখন আমাদের কাছে ছুরি-চাকু থাকে না, থাকে শানিত পাথর বা বাশের খণ্ড। তখন আমরা কি করব? রাসূল (সা) বললেন : রক্ত প্রবাহিত কর যে জিনিস দ্বারাই সম্ভব হোক এবং তার উপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ কর। (মুসনাদে আহমাদ, আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ)
২. গলদেশে ছুরি চালাতে হবে অথবা গলার নিচের অংশে ছুরি বসিয়ে দিতে হবে, (প্রচলিত ভাষায় এটাই নহর) যার ফলে জন্তুটির মৃত্যু সঙ্ঘটিত হবে।
যবেহর পূর্ণতার পন্থা হচ্ছে, খাদ্যনালী ও গলার মধ্যের বড় দুটি রগ কেটে দিতে হবে। কিন্তু যখন নির্দিষ্ট স্থানে ছুরি চালান অসম্ভব হয়ে পড়বে, যেমন একটা গুরু কুয়ার মধ্যে পড়ে গেছে, তার মাথা ভিতরে, পায়ের দিকটা বাইরে রয়েছে স্বাভাবিক নিয়মে যথাস্থানে যবেহ করা যাবে না। তখন তার অবস্থা হবে শিকার করা জন্তুর মতো। তখন ধারাল অস্ত্র সাধ্যমত যে কোন স্থানে চালিয়ে রক্ত প্রবাহিত করেত হবে। তা করা হলে হালাল হয়ে যাবে।
বুখারী-মুসলিমে হযরত রাফে ইবনে খদীজা (রা) থেকে হাদীস উদ্বৃত হয়েছে। তিনি বলেন:
(আরবী**************)
এক পরিভ্রমণে আমরা নবী করীম (সা) এর সঙ্গে ছিলাম। সহসা একটি উট নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেল। তখন লোকদের সঙ্গে ঘোড়া ছিল না বলে দ্রুত গতিতে গিয়ে সেটাকে ধরা গেল না। এক ব্যক্তি তীর নিক্ষেপ করে উটকে বেঁধে ফেলল। তা দেখে নবী করীম (সা) বললেন : এসব চতুষ্পদ জন্তু এভাবে আয়াত্তের বাইরে চলে গেলে তখন তোমরাও তার অনুরূপ আচরণই করবে।
৩. যবেহ করার সময় আল্লাহ ছাড়া আর কারো নাম উচ্চারণ করা যাবে না। এ এক সর্ববাদী সম্মত কথা। তার কারণ হচ্ছে, জাহিলিয়াত যুগে লোকেরা তাদের উপাস্যদের দেবী দেবতা-মূর্তির নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে জন্তু যবেহ করত। যবেহ করার সময় তারা সে সব দেব-দেবীর নাম উচ্চারণ করত অথবা নির্দিষ্ট স্থানে বলিদান করত। কুরআন মজিদে এসব হারাম করা হয়েছে। পূর্বেই এতদসংক্রান্ত আয়াতের উল্লেখ করা হয়েছে।
৪. যে জন্তুটি যবেহ করা হচ্ছে, তার উপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করতে হবে। কুরআনের আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় বলে দেয়া হয়েছে এ ভাষায় : (আরবী**********************)
তোমরা যদি আল্লাহর আয়াতসমূহের প্রতি ঈমানদার হয়ে থাক, তাহলে যেসব জন্তু যবেহ করার সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয়েছে তোমরা সেগুলো খাও। (সূরা আন’আম : ১১৮)
ইরশাদ হয়েছে : (আরবী******************)
যেসব জন্তু যবেহকালে আল্লাহরও নাম উচ্চারণ করা হয়নি, তোমরা তা খেও না। কেননা তা খাওয়া ফাসিকী (ইসলামের সীমালংঘনমূলক কাজ।
রাসূলে করীম (সা) বলেছেন: (আরবী*************************)
যে জন্তুর রক্ত প্রবাহিত করা হয়েছে এবং তখন তার উপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয়েছে, তোমরা তা খাও। (বুখারী)
যেসব হাদীসে শিকার করার উদ্দেশ্যে তীর নিক্ষেপ করার এবং শিক্ষা দেয়া কুকুরকে শিকারের উদ্দেশ্যে পাঠাবার সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করার কথা বলা হয়েছে, তা উপরিউক্ত মতেরই সমর্থক। কোন কোন আলেমের মতে আল্লাহর নাম উচ্চারণ তো জরুরী; কিন্তু ঠিক যবেহ করার মূহুর্তেই এ নাম নিতে হবে, এমনটা প্রয়োজন নয়। খাওয়ার সময় নাম উচ্চারণও যথেষ্ট। কেননা যে লোক খাওয়ার সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে সে তো নিশ্চয়ই এমন জিনিস খায় না, যার উপর আল্লাহ নাম উচ্চারণ করা হয়নি। হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেছেন : (আরবী***********************)
নতুন ইসলাম গ্রহণকারী কিছু লোক নবী করীম (সা) কে জিজ্ঞাসা করলেন, লোকেরা আমাদের নিকট গোশত নিয়ে আসে, তারা তার ওপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করেছিল কিনা, তা আমাদের জানা নেই। এক্ষণে আমরা তা খাব, না খাব না? নবী করীম (সা) জবাবে বললেন : তামরা আল্লাহর নাম উচ্চারণ কর এবং খাও। (বুখারী)
যবেহ করার এ নিয়মের তাত্পর্য
জন্তু যবেহ করার এরূপ বিধিবদ্ধ করার মৌল কারণ হচ্ছে, জন্তুটির প্রাণ যেন এমনভাবে সংহার করা হয়, যাতে করে সেটির কম সে কম কষ্ট ভোগ হয়। যবেহর অস্ত্রটি খুব ধারাল হওয়ার ও গলদেশে যবেহ করা শর্ত এ জন্যেই করা হয়েছে। কোননা এসব জিনিস দ্বারা যবেহ করা হলে জন্তুটির কণ্ঠদেশ রুদ্ধ করার মতো অবস্থা হয়। নবী করীম (সা) ছুরিটিকে অতিশয় ধারাল বানানো এবং জন্তুটিকে শান্তি দাদের নির্দেশ দিয়েছেন। বলেছেন : (আরবী************************)
আল্লাহ তা’আলা প্রতিটি ব্যাপারে এ ক্ষত্রে দয়াশীলতা অবলম্বন ফরয করে দিয়েছেন। কাজেই তোমরা যখন হত্যা করবে, তখন অবশ্যই দয়াশীলতা সহকারে হত্যা করবে। আর যখন যবেহ করবে, তখনও সুন্দর ও উত্তমভাবে যবেহ করবে। তোমাদের প্রত্যেকেরই কর্তব্য যবেহ করার সময় যার যার ছুরিকে খুব ধারাল বানিয়ে নেয়া এবং যবেহ করার পর সেটাকে ধীরে ধীরে প্রশান্তি লাভ করার সুযোগ দেয়া। (বুখারী)
এ সহানুভূতি ও দয়াশীলতা পর্যায়ে হযরত ইবনে উমর বর্ণিত একটি হাদীসে উল্লেখ্য। তিনি বলেন :
(আরবী**********)
নবী করীম (সা) আদেশ করেছেন ছুরি শানিত করতে এবং অপরাপর জন্তু থেকে গোপন রাখতে। তাই বলেছেন: তোমাদের কেউ যখন যবেহ করার কাজ করবে, তখন তা যেন সম্পূর্ণতায় পৌছায়। (ইবনে মাযাহ)
হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, এক ব্যক্তি একটি বকরী শোয়ায়ে তার ছুরিতে ধার দিতেছিল্ তা দেখে নবী করীম (সা) বললেন : (আরবী***********************)
তুমি কি বকরীটিকে কয়েকবার মারতে চাও? ওটিকে শোয়াবার আগে কেন তুমি তোমার ছুরিকে শানিত করে নাও নি। (হাকেম)
হযরত উমর (রা) দেখতে পেলেন, এক ব্যক্তি তার পা দিয়ে চেপে ধরে তার বকরীটিকে হেঁচড়িয়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছে যবেহ করার উদ্দেশ্যে। তখন তিনি লোকটিকে বললেন : (আরবী**********************)
তোমার জন্যে দু:খ! তুমি বকরীটিকে খুব ভালভাবে মৃত্যুর দিকে নিয়ে যাও।
এ পর্যায়ে ইসলামী চিন্তাধারা সাধারণভাবে এরূপেই আমরা পাচ্ছি। আর তা হচ্ছে, বোবা জন্তুর প্রতি দয়াশীলতা এবং ওটিকে সব রকমের কষ্ট থেকে নিষ্কৃতি দেয়া – যতটা সম্ভব।
জাহিলিয়াতের যুগে লোকেরা উষ্ট্রের ঝুটি (Hamp) জীবন্ত অবস্থায় কেটে নিয়ে খেতে খুব ভালবাসত। আর তারা জীবন্ত অবস্থায় দুম্বার পিছণে ঝুরে থাকা চাকতি কেটে নিয়ে যেত। তাতে করে ওদের কষ্টের সীমা থাকত না। এ করণে নবী করীম (সা) জীবন্ত জন্তুর দেহাংশ কেটে নেয়াকে হারাম করে দিয়েছেন । বলেছেন :
(আরবী*******************)
জন্তুর জীবন্ত অবস্থায় তার দেহাংশ কেটে নেয়া হলে সেটাকে মৃত মনে করতে হবে (এবং তা হারাম) । (আহম্মদ আবু দাউদ, তিরমিযী)
যবেহ করার সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণের তাত্পর্য
যবেহ করার সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করার অপরিহার্যতার মূলে গভীর সূক্ষ্য কারণ নিহিত। সে বিষয়ে অবহিত হওয়া ও সে দিকে লক্ষ্য দেয়া বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে।
মূর্তিপূজারী ও জাহিলিয়াতের লোকেরা যবেহ করার সময় তাদের মা’বুদদের নাম উচ্চারণ করত। ইসলামে তদস্থলে আল্লাহর নাম উচ্চারণের বিধান দেয়া হয়েছে। কেননা মুশরিকরা যখন যবেহ করার সময় তাদের উপাস্যদের নাম লয়, তখন এক আল্লাহর প্রতি ঈমানদার লোকেরা অনুরূপ সময়ে তা না করে কি থাকতে পারে?
দ্বিতীয়ত : জন্তুগুলোও তো মানুষেরই মতো এক আল্লাহর সৃষ্টি। মানুষ যে ওগুলোর প্রাণ হরণ করবে, তাতে আল্লাহর অনুমতি থাকা একান্তই আবশ্যক। যবেহ করার সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হলে এই অনুমতি লাভেরই ঘোষণা হয়ে যায়। এ সময় সে যেন বলছে, আমি এ কাজটি করছি এ জন্যে নয় যে, ওগুলো দুর্বল, অক্ষম ও অসহায়ক। আমি ওগুলোর ওপর জুলুম করতে চাইলে। বরং যবেহ করার এই যে কাজটি আমি করছি, তা একমাত্র আল্লাহর অনুমতিক্রমেই করছি। তার নাম নিয়েই আমি শিকার করছি এবং তাঁরই নাম সহকারে আমি তা খাচ্ছি।
ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানদের যবেহ করা জন্তু
জন্তু যবেহ করার ব্যাপারে ইসলাম কত কড়াকড়ি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে, তা আমরা এর পূর্বে দেখেছি। বস্তুত ইসলামে এ ব্যপারটি অত্যন্ত গুরুত্ববহ। আরব মুশরিক ও জাহিলিয়াতের লোকেরা জন্তু যবেহ করার ব্যাপারটিকে তাদের আকীদা অনুযায়ী ধর্মের অঙ্গ ও পূজা-উপাসনার অপরিহার্য অনুষ্টানের মধ্যে গণ্য করে নিয়েছিল। তারা জন্তু যবেহ করে আসলে তাদের দেবদেবী-উপাস্যদের সন্তুষ্টি ও নৈকট্যই অর্জন করতে চেয়েছে। এই কারণে দেবদেবীর উদ্দেশ্যে বলিদানের জন্যে নির্দিষ্ট স্থানেই তারা জন্তু যবেহ করত। আর তখন তাদের দেবদেবীর নাম উচ্চারণ করত।
ইসলাম এসব বন্ধ করে দিয়ে যবেহ করার সময় একমাত্র আল্লাহর নাম উচ্চারণ করার ব্যবস্থা দৃঢ়ভাবে স্থাপিত ও কার্যকর করল। আল্লাহ ছাড়া অপর কারো নাম লওয়াকে সম্পূর্ণ নিষেধ করে দিল। ওসব নির্দিষ্ট স্থান সমূহে জন্তু যবেহ করা এবং এক আল্লাহ ছাড়া অন্যদের নামে উত্সর্গীকৃত জন্তু হারাম করে দিয়েছে।
আহলি কিতাব- ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানরা- মূলত তাওহীদে বিশ্বাসী ছিল। কিন্তু পরে তাদের ঈমানী আকীদায় শিরক অনুপ্রবেশ করে। কেননা তাদের কাছে সে দ্বীনের দাওয়াত পৌছেছিল এমন সব লোকের মাধ্যমে, যারা শিরক-আকীদায় দোষ ও মালিন্য থেকে নিজেদের বিশ্বাস ও মনমানসকে মুক্তি করে নিতে পারেনি। এ কারণে মুসলিমদের মনে এ ভাবটা জেগে উঠার খুব বেশি সম্ভাবনা ছিল যে, ওদেরকে মূর্তিপূজারী মুশরিক মনে করে তদনুরূপ আচরণই ওদের সাথে অবলম্বন করতে হবে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা ওদের ব্যাপারে মূর্তিপূজারীদের থেকে ভিন্নতর রীতি অবলম্বন করার নির্দেশ দিলেন। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে ওদের সাথে একত্রিত হওয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে, যেমন অনুমতি দেয়া হয়েছে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের। আল্লাহ তাআলা কুরআনের সর্বশেষ অবতীর্ণ আয়াতে ইরশাদ করেছেন : (আরবী********************)
আজকের দিনে তোমাদের জন্যে সব পবিত্র উত্কস্ট খাদ্য হালাল করে দেয়া হলো, আর তাদের খাদ্যও, যাদের কিতাব দেয়া হয়েছে- তোমাদের জন্যে হালাল এবং তোমাদের খাদ্যও হালাল তাদের জন্যে। (সূরা মায়িদা : ৫)
এক কথায় এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে সকল প্রকার পবিত্র উত্কৃস্ট খাদ্য সম্পূর্ণ হালাল। অতএব বহীরা‘ সায়েরা‘ আসীলা, বা হাম‘ বলতে আর কিছু নেই। আর ইয়াহুদী খ্রিস্টান আহলি কিতাব জাতিগুলোর খাদ্য মৌলিকভাবে তোমাদের জন্যে হালাল। আল্লাহ তা কখনই হারাম করেন নি। তোমাদের খাদ্যও তাদের জন্যে হালাল। তাহলে তাদের যবেহ করা বা শিরক করা জন্তুর গোশত খাওয়াও তোমাদের জন্যে জায়েয। অনুরূপভাবে তোমরা যা যবেহ কর বা শিরক কর তা তাদের খাওয়াতেও কোন নিষেধ নেই।
তবে আরবের মুশরিকদের ব্যাপারে ইসলাম খুব বেশি কঠোরতা অবলম্বন করেছে। কিন্তু আহলি কিতাবের সাথে নম্র আচরণ গ্রহণ করেছে। তার কারণ হচ্ছে, আহলি কিতাব লোকেরা ওহী, নবুওয়্যাত এবং মোটামুটি দ্বীনের মৌলিক নিয়ম নীতিগুলো মানে। এ কারণে তারা ঈমানদারদের খুবই নিকটে অবস্থিত। খাওয়া-দাওয়ায় তাদের সাথে শরীক হওয়া, তাদের কন্যা বিয়ে করা এবং তাদের সাথে মিলমিশ করা শরীয়তসম্মত বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এতে করে তাদের জন্যে সুযোগ দেয়া হয়েছে যে, তারা ইসলামকে লোকদের ঘরে, কথা ও কাজ, নৈতিকতা ও লেনদেনের ক্ষেত্রে তা আসল রূপে প্রত্যেক্ষ করার সুযোগ পাবে। এ উপায়েই তারা জানতে পারবে যে, মূলত ইসলাম এমন এক দ্বীন, যা উচ্চতর তত্ত্ব ও সত্য, পূর্ণাঙ্গ নিয়মাদি, অতীব উত্তম বিশ্বাস ব্যবস্থা সমূহের ওপর ভিত্তিশীল। এতে শিরক ও অর্থহীন কথাবার্তার কোন স্থান নেই।
কুরআনে ঘোষণা : (আরবী*****************)
কিতাবপ্রাপ্ত লোকদের খাদ্য।
কথাটি খুবই সাধারণ ও ব্যাপক অর্থ জ্ঞাপক। সর্বপ্রকারের খাদ্যই এর অন্তর্ভূক্ত। ওদের যবেহ করা জন্তুর গোশত এবং অন্যান্য খাদ্য সবই হালাল। কাজেই এ সবকিছুই আমাদের স্থায়ীভাবেই হালাল। তবে যদি হারাম করে দেয়া হয়ে থাকে যেমন মৃত জন্তু, প্রবাহিত রক্ত শূকরের গোশত- এগুলো খাওয়া জায়েয নয়। এটা সর্ববাধিসম্মত মত। তা যে কোন কিতাবী লোকের কাছেই হোক কিংবা হোক কোন মুসলিমের কাছে- তাতে কোন পার্থক্য নেই।
তবে এখানে কতগুলো বিষয় বিশেষভাবে মুসলমানদের জন্যে বিবেচনা প্রয়োজন।
১. গির্জা ও মেলাতে হারের জন্যে যবেহ করা জন্তু
কোন কিতাবী লোক সম্পর্কে যতক্ষন না জানা যাবে যে, সে যবেহ করার সময় ঈসা-মসীহ বা উজাইর প্রভৃতি অ-আল্লাহর নাম উচ্চারণ করেছে ততক্ষণ পর্যন্ত তা যবেহ করা জন্তুর গোশত খাওয়া হালাল। কিন্তু যখন জানা যাবে যে, সে যবেহ করার সময় অ-আল্লাহর নাম উচ্চারণ করেছে, তখন সেই বিশেষ জন্তুটি হারাম হয়ে যাবে বলে ফিকাহবিদগণ মত প্রকাশ করেছেন।
তবে কেউ কেউ বলেছেন : আল্লাহ তো ওদের খাদ্য আমাদের জন্যে হালাল করেই দিয়েছেন। এখন তারা যবেহ করাকালে কি বলে, কার নাম উচ্চারণ করে তা আল্লাহই ভাল জানেন। (সেদিকে লক্ষ্য দেয়ার প্রয়োজন নেই)
আহলি কিতাবের ঈদ উত্সব ও গীর্জা ইত্যাদি অনষ্ঠান উপলক্ষে যবেহ করা জন্তু সম্পর্কে ইমাম মালিকের কাছে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন : (আরবী***********)
আমি তা খাওয়া মাকরূহ মনে করি না। [ইমাম মালিকের মাযহাবে এটাই ফতোয়া। তিনি এ কালের কোন কোন আলেমের ন্যায় হারাম ঘোষণায় খুব তাড়াহুড়া করতেন না। শুধু মাকরূহ বলেই ক্ষন্ত থাকতেন।]
তাঁর এই মাকরূহ মনে কারাটা তাঁর নিজস্ব অতিরিক্ত তাকওয়ার ব্যাপার। তাঁর সন্দেহ হয়েছে অ-আল্লাহর নামে যবেহ হওয়ার। তাই তিনি তা খাওয়া মাকরূহ মনে করেছেন। কিন্তু তিনি তা হারাম মনে করেন নি। কেননা তাঁর মতে আহলি কিতাবের ক্ষেত্রে অ-আল্লাহর নামে যবেহ করার অর্থ হচ্ছে তারা তাদের উপাস্যদের উপাসনা ও তাদের নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে যে জন্তু যবেহ করে সে জন্তু তারা নিজেরা খায় না। তাবে যেসব জন্তু তারা নিজারা খাওয়ার উদ্দেশ্যে যবেহ করে তা তাদের খাদ্যের মধ্যে গণ্য আর তা আমাদের জন্যে হালাল বলে নিজেই ঘোষনা করেছেন। [মুগনী কিতাবে আছে যে, যদি কোন আহলি কিতাব যবেহ করার সময় জ্ঞাতসারে আল্লাহর নাম উচ্চারণ না করে তবে তার যবেহ করা পশু খাওয়া হালাল নয়। হযরত আলী (রা) থেকে এটাই বর্ণিত হয়েছে।
ইমাম শাফেয়ী, নাখয়ী, হাম্মাদ, ইসহাক এবং হানাফী মতাবলম্বিগণের মতও এটাই। আহলি কিতাবের খাদ্য হালাল হওয়া সম্পর্কিত কুরআনের আয়াতের মর্ম এই যে, তাদের যবেহ করা ঐসব পশু খাওয়া হালাল যাতে যবেহের নির্ধারিত শর্তগুলো পূর্ণ করা হয়েছে- যেমনিভাবে মুসলমানদেরকেও পূর্ণ করতে হয়। হাঁ তবে একথা সঠিকভাবে জানা যায় যে, যবেহকারী আল্লাহর নাম নিয়েছে বা নেয়নি কিংবা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নাম নিয়েছে অথবা নেয়নি তবে তার যবেহ করা পশু খাওয়া হালাল। কেননা আমাদের জন্যে আল্লাহ তা‘আলা মুসলমান এবং আহলি কিতাবের যবেহ করা পশু হালাল করেছেন। বন্তুত আল্লাহ তা’আলা জানেন যে, আমরা প্রত্যেক যবেহকারী ব্যক্তির অবস্থঅ সম্পর্কে অবগত হতে পারি না। (আল-মুণনী : ৮ম খণ্ড, পৃ. ৫৭১)]
২. বিদ্যুত্ স্পর্শে যবেহ করা বা টিনবদ্ধ গোশত খাওয়া
দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে, আহলি কিতাব- ইয়াহুদ-খ্রিস্টানদের যবেহ করার নিয়ম কি আমাদের নিয়মের অনুরূপ হতে হবে? আমারা যেমন তীক্ষ্ণ অস্ত্র দ্বারা গলা কেটে দিই, ওদের যবেহেও কি এ রকমেরই হতে হবে?
অধিকাংশ বিশেষজ্ঞই এ ব্যাপারে এ শর্তটি আরোপ করেছেন। তবে মালিকী মাযহাবের আলেম জামায়াত ফতোয়া দিয়েছেন যে, তা জরুরী শর্ত নয়।
কাযী ইবনুল আরাবী সূরা আল-মায়িদার আয়াতের তাফরীরে বলেছেন :
একথা অকাট্যভাবে প্রমাণ করে যে, আহলি কিতাবের শিকার ও খাবার আল্লাহর জায়েয হলে ঘোষিত জিনিসগুলোর মধ্যে গণ্য। তা নি:শর্তে হালাল। একথাটি বিশেষভাবে বলা হয়েছে, যেন এ ব্যাপারে সব শোবাহ সন্দেহ দূরীভূত হয়ে যায়, ভুল ধারণার লেশমাত্র অবিশষ্ট না থাকে। আমার নিকট জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, খ্রিস্টানরা মুরগীর গলা মুচড়িয়ে দিয়ে মারে। পরে তারা তা রান্না করে। এরূপ অবস্থায় কি আমরা তাদের সাথে খাবারে শরীক হতে পারি? ওদের খাবার কি খাওয়া যেতে পারে? আমি বললাম, খাওয়া যেতে পারে। কেননা তা খ্রিস্টান এবং তাদের পাদ্রী-পণ্ডিতদের খাবার। যদিও আমাদের মতে যবেহ করার এ নিয়াম ঠিক নয়। কিন্তু আল্লাহ তো ওদের খাবার আমাদের জন্যে সাধারণভাবে হালাল করে দিয়েছেন। আর ওরা ওদের দ্বীনে যেখানেই জায়েয মনে করে, তা আমাদের জন্যেও হালাল। তবে সে সব আহার্য আল্লাহ তাআলা ওদেরকে মিথ্যাবাদী বলেছেন, সেগুলো খাওয়া যাবে না। আমাদের বিশেষজ্ঞগণ বলেছেন, এ আহলি কিতাবরা ওদের কন্যাদের আমাদের কাছে বিয়ে দেয়। তাদের সাথে সঙ্গম জায়েয। এমতবস্থায় ওদের যবেহ করা জন্তু আমরা খাব না কেন? হালাল-হারামের দৃষ্টিতে বিবেচনা করা হলে যৌন সঙ্গমের তুলনায় খাদ্য খাওয়ার ব্যাপারটি অনেক কম গুরুত্বপূর্ণ কাজ।
এ তাফসীরকারই অপর এক স্থানে লিখেছেন :
ওরা যবেহ করে না, গলায় ফাঁস দিয়ে বা মাথা নিষ্পেষিত করে মারে । তারপর ওরা তা খায়। এ কারণে তা আমাদের জন্য মুর্দার ও হারাম। কিন্তু ও (নাজায়েয হওয়া ও উপরে বর্ণিত জায়েয হওয়ার) ব্যাপারদ্বয়ের মাঝে কোন বৈপরীত্য নেই। কেননা আহলি কিতাব যেটিকে সঠিক যবেহ মনে করে তা খাওয়া আমাদের জন্যে অবশ্যই হালাল হবে। যদিও আমাদের দৃষ্টিতে ওদের যবেহ করার এ নিয়ম ঠিক নয়। কিন্তু যে সম্পর্কে ওরা নিজেরাই মনে করে, এ যবেহটা ঠিক নয়, তা আমাদের জন্যেও হালাল নয়। যবেহ অর্থ জন্তুটির প্রাণ বের করা হবে ওটি খাওয়া হালাল-করণের ইচ্ছায়।’
মালিকী মাযহাবের অনুসারী একটি জামায়াতের এই মত।
এ আলোচনার আলোকে আমরা আহলি কিতাব লোকদের টিনবন্দী ও সংরক্ষিত মোরড় বা গরুর গোশত সম্পর্কিত শরীয়তের নির্দেশ বুঝতে পারি। ওদের দেশে মোরগগুলো বিদ্যুত্ স্পর্শে যবেহ করার কাজ করা হয়। এ গুলোকে ওরা নিজেরা যতক্ষণ হালাল খাদ্য মনে করতে থাকবে, আয়াতটির সাধারণ ঘোষণা অনুসারে তা আমাদের জন্যে হালাল বিবেচিত হতে থাকবে। [কিন্তু এ কথাটি সর্ববাদীসম্মত নয়। সাধারণভাবেই জানা আছে যে, টিনবন্দী গোশত শরীয়ত মুতাবিক যবেহ করা জন্তু বা প্রাণীর নয়। এক কোপে কাটা বা যবেহ করার সময় সচেতনভাবে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয়নি, তা কেবলমাত্র আহলি কিতাব লোকদের মনে করলেই আমাদের জন্যেও হালাল হতে পারে না। সাধারণত যে রকমটা হয়ে থাকে, সে দৃষ্টিতে ফতোয়া দেয়া আবশ্যক। তাই যে জন্তু শরীয়তসম্মত নিয়মে যবেহ করা হয়নি তা খাওয়া জায়েয নয়। তার যবেহকারী মুসলিম হলেও নয়। -(অনুবাদক)]
তবে কমিউনিষ্ট দেশসমূহে তৈরী টিনবন্দী গোশত খাওয়া আমাদের জন্যে আদৌ জায়েয হতে পারে না। কেননা ওরা ধর্ম নামের সব কিছুকেই অবিশ্বাস ও অস্বীকার করেছে। কাজেই ওরা আহলি কিতাব এর মধ্যে গণ্য নয়।
অগ্নি পূজক প্রভৃতির যবেহ করা জন্তু
অগ্নিপূজক বা প্রাচীন পারসিক ধর্মাবলম্বীদের যবেহ করা জন্তুর গোশত খাওয়া সম্পর্কে ইলমওয়ালারা বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। অনেকেই তা খেতে নিষেধ করেছেন কেননা ওরা আসলে মুশরিক। অপরাপর মণীষীরা বলেছেন, তা খাওয়া হালাল। কেননা নবী করীম (সা) বলেছেন : (আরবী******************)
ওদের সাথে আহলি-কিতাব সুলভ আচরণ করো। (মালিক, শাফী)’
এ কারণেই হিজর নামক স্থানের অগ্নিপূজারীদের কাছ থেকে জিযিয়া নেয়া হয়েছিল। (বুখারী)
ইবনে হাজম তাঁর আল-মুহলা গ্রন্থে লিখেছেন : (আরবী**********************)
ওরাও আহলি কিতাব। অতএব সর্ব ব্যাপারে ওদের সাথে আহলি কিতাবের ন্যায় আচরণ গ্রহণ করতে হবে। [জমহুর আলিমদের মতে মজুসী- অগ্নিপূজক বা পারসিকদের যবেহ করা জন্তু খাওয়া জায়েয নয়। হযরত ইবনে মাসউদ, হযরত ইবনে আব্বাস, হযরত আলী, হযরত জাবির, ইমাম মালিক, ইমাম জুহরী, ইমাম শাফিয়ী, হানাফী ফিকাহবিদগণ এবং ইমাম আহমদ প্রমুখ এ মত প্রকাশ করেছেন। ইবনে কুদামাহর মতে নবী করীম (সা) এর উপরিউক্ত উক্তি ‘ওদের সাথে আহলি কিতাবের ন্যায় আচরণ গ্রহণ কর‘ কথাটি কেবলমাত্র জিযিয়া ধার্য করা পর্যায়ে প্রযোজ্য। ওদের যবেহ করা জন্তু খাওয়া ও ওদের মেয়ে বিয়ে করার ব্যাপারে এ নির্দেশ নয়। (আরবী************************)
আল্লামা জাসসাস বলেন, মুজসীদের সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। অধিকাংশ ফিকাহবিদের মতে ওরা আহলি কিতাব নয়। খুব কম লোকই ওদের আহলি কিতাব মনে করে। কুরআনে মাত্র দুটি সম্প্রদায়কে আহলি কিতাব বলা হয়েছে। মজুসীদেরও আহলি কিতাব গণ্য করে দুটির পরিবর্তে তিনটি সম্প্রদায়ের কথা বলা হতো। নবী করীম (সা) ও ওরা আহলি কিতাব একথা বলেনে নি। আহলি কিতাবের ন্যায় আচরণ করতে বলেছেন মাত্র। আর তাও ওদের কাছ থেকে জিযিয়া আদায় করার ব্যাপারে । (আরবী*********) – অনুবাদক।]
ইমাম আবু হানিফার মতে ছাবী ধর্মাবলম্বীরা আহলী কিতাব। (অনেকে ব্রাহ্মণদেরও আহলি কিতাব মনে করে। বলা হয়, ওদের প্রতি কিতাব নাযিল হয়েছিল, যদিও তারা হারিয়ে ফেলেছে।)
দৃষ্টির অন্তরালবর্তী জিনিসের খোঁজ করা অনাবশ্যক
যা চোখের অন্তরালে অবস্থিত, সে বিষয়ে প্রশ্ন করা ও খোঁজ খবর লওয়ার জন্যে চেষ্টা করা- কিভাবে যবেহ করা হয়েছে, যবেহের সব কয়াটি শর্ত পূর্ণ হয়েছে কিনা, যবেহ কালে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয়েছে কিনা- এ ধরণের অজানা বিষয়সমূহ জানতে চেষ্টা করা মুসলিম ব্যক্তির দায়িত্বভুক্ত নয়। কেননা মুসলিম ব্যক্তি যবেহ করে থাকলে অপরাপর অজানা বিষয়াদি- সে অজ্ঞ-মূর্খ, ফাসিক বা কিতাবী- যাই হোক না কেন, তা খাওয়া সম্পূর্ণ হালাল। পূর্বেই বলা হয়েছে, সাহাবীগণ প্রশ্ন করলেন, ইয়া রাসূল, লোকেরা আমাদের কাছে গোশত নিয়ে আসে, তারা যবেহ কালে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করেছে, কি করেনি তা আমরা জানি না, এ অবস্থায় কি করব? রাসূল বললেন : তোমরা বিসমিল্লাহ বলে আহার কর।
এ হাদীস সম্পর্কে বিশেষজ্ঞগণ বলেছেন :
এ হাদীসটি প্রমাণ করে যে, কাজ কর্ম ও হস্তক্ষেপ ইত্যাদি সব কিছুই যথার্থ ও ঠিকঠাক আছে মনে করতে হবে, যতক্ষণ তার খারাপ বা বাতিল হওয়ার অকাট্ট দলিল পাওয়া যাবে।
শিকার
আরব ও দুনিয়ার অন্যান্য জাতিগুলোর বিপুল সংখ্যক লোকই শিকার কার্যের ওপর নির্ভরশীল হয়ে জীবন যাবন করছে। এ কারণে কুরআন ও সুন্নাতে এ বিষয়টির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ফিকাহ গ্রন্থ রচয়িতাগণ নিজ নিজ গ্রন্থে এজন্যে স্বতন্ত্র্য অধ্যায় রচনা করেছেন। তাঁরা এর মধ্যে কি হালাল ও কি হারাম, এ ক্ষেত্রে কি ওয়াজিব কি মুস্তহাব, তা বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। এভাবে বিস্তারিত বলার প্রয়োজনও ছিল। কেননা যে সব জন্তু বা পাখির গোশত পবিত্র ও উত্কষ্ট তার অনেক গুলোই এমন যে, তা মানুষের আওতাধীন থাকে না। তা ধরা ও কাবু করাও সহজসাধ্য নয়। কেননা সেগুলো মানুষের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত নয়। এ কারণে ইসলাম আয়ত্তাধীন জন্তু প্রাণী যবেহ করার ব্যাপারে গলায় বা গলার নিম্ন দেশে ছুরি চালানোর যে শর্ত আরোপ করেছে, এসব জন্তু-প্রাণী হালাল হওয়ার জন্যে সে ধরনের শর্ত আরোপ করা হয়নি। বরং সেগুলো যবেহ করার জন্যে সহজ পন্থা নির্ধারণ করেছে। এতে করে মানুষের কষ্ট অনেকটা লাঘব করা হয়েছে এবং খাদ্যের ক্ষেত্রে প্রশস্ত করা হয়েছে।
ইসলাম মানুষের স্বাভাবিক প্রয়োজন সমূহের প্রতি পূর্ণমাত্রায় দৃষ্টি রক্ষা করেছে। এ পর্যায়ে যে সব শর্ত আরোপিত হয়েছে তার উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষ ইসলামের মৌল বিশ্বাস ও তার বিধান ব্যবস্থা সমূহের কাছে আত্মসমর্পণ করুক। আর একজন মুসলিমকে যেমন সর্ব ব্যাপারে ও ক্ষেত্রে ইসলামের নিয়ামাদি পালন করতে হয়, এক্ষেত্রেও যেন সে ইসলামের নিয়মগুলো যথাযথভাবে পালন করে।
এ পর্যায়ের কতগুলো শর্ত হচ্ছে শিকারকারী সংক্রান্ত, কতগুলো শিকার করা জীব সংক্রান্ত এবং কতকগুলো শিকার কার্য সংক্রান্ত।
এখানে স্থলভাগের প্রাণী শিকার সম্পর্কে বলা হচ্ছে। জলভাগের শিকার সম্পর্কে তো ইতিপূর্বে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। আর তার সারকথা হচ্ছে, কোনরূপ নিষেধ ছাড়াই সব কিছুকে আল্লাহ তা‘আলা হালাল করে দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে :
(আরবী***************)
সামুদ্রিক শিকার ও সেখানে থেকে পাওয়া খাদ্যই তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে। (সূরা মায়িদা : ৯৬)
শিকারী সম্পর্কিত কথা
স্থলভাগে শিকারীর জন্যে সেই শর্ত যা যবেহকারীর জন্যে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। আর তা হচ্ছে, তাকে মুসলিম হতে হবে অথবা আহলি কিতাব। আহলি কিতাব পর্যায়ে পড়ে এমন লোকের শিকারও খাওয়া যাবে- যেমন দাবি ও মাজুসী।
ইসলামের শিক্ষা হচ্ছে, নিরর্থক শিকার করা অর্থাত্ খাওয়ার উদ্দেশ্য না নিয়ে অথবা অপর কোন সুফল পূর্ণ কাজের উদ্দেশ্যে না রেখে শিকার করা বাঞ্ছনীয় নয়। কেননা বিনা কারণে ও উদ্দেশ্যহীনভাবে প্রাণী হত্যা করার অনুমতি ইসলাম দেয়ানি। হাদীসে বলা হয়েছে : (আরবী********৯৫***********)
যেলোক কোন পাখি অর্থহীন উদ্দেশ্যহীনভাবে হত্যা করবে, কিয়ামতের দিন তা আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করবে, হে আল্লাহ অমুক লোকটি আমাকে অর্থহীনভাবে হত্যা করেছিল, কোন ফায়দা লাভের জন্যে হত্যা করেনি।
অপর একটি হাদীসে বলা হয়েছে : (আরবী***********************)
যে লোক কোন চড়ুই বা তার বড় কোন পাখি অন্যায়ভাবে হত্যা করবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার বিষয়ে নিশ্চয়ই কৈফিয়ত চাইবেন। সাহাবী বললেন হে রাসূল, ওদের আবার কি হক রয়েছে? বললেন : ওদের হক হচ্ছে ওদের যবেহ করে খেতে হবে, ওদের মস্তক কেটে নিক্ষেপ করে দেয়া নয়।
শিকারীর জন্যে আরও শর্ত হচ্ছে, সে যেন হজ্জ কিংবা উমরার জন্যে ইহরাম বাধা অবস্থার লোক না হয়। কেননা ইহরাম বাধা অবস্থায় মুসলিম পূর্ণাঙ্গ শান্তি নিরাপত্তা ও বিপদ মুক্তির অবস্থায অবস্থান করে। এ ব্যাপারে তার ক্ষেত্রে অত্যান্ত প্রশস্ত। তার চারপার্শ্বের সব জীব এবং পাখিরাও পূর্ণ নিরাপত্তা লাভ করে থাকে। এমন কি ইহরাম বাধা মুসলিমের হাতের বা তীরের নাগালের মধ্যেও যদি কোন শিকার এসে যায়, তবুও সে শিকার থেকে বিরত থাকবে। এ হচ্ছে মুসলিমের ধৈর্যের প্রশিক্ষণ পর্যায়ের ব্যবস্থা। তাই কুরআনে বলা হয়েছে : (আরবী***********************)
হে ঈমানদার লোকেরা, আল্লাহ শিকার জাতীয় জিনিস দ্বারা তোমাদের অবশ্যই পরীক্ষা করবেন। তোমাদের হাত ও তীর তা নাগালের মধ্যে পেয়ে যাবে। আল্লাহকে অজ্ঞাতসারে কে সে ভয় করে, তা তিনি জানতে চান। এতদসত্ত্বেও যদি কেউ সীমালংঘন করে, তবে তার জন্যে পীড়াদায়ক আযাব রয়েছে।
(আরবী********************)
হে ঈমানদার লোকেরা ! তোমরা ইহরাম বাঁধা থাকা অবস্থায় শিকার করবে না। (সূরা মায়িদা : ৯৫)
(আরবী*******************)
তোমরা যতক্ষণ ইহরাম বাধা অবস্থায় থাকবে, ততক্ষন তোমাদের জন্যে স্থলভাগে শিকার করা হারাম করা হয়েছে। (সূরা মায়িদা:৯৬)
শিকার প্রাণী সম্পর্কিত শর্ত
যে জন্তু বা প্রাণী শিকার করা হবে, সে সম্পর্কে শর্ত হচ্ছে, তা এমন জন্তু বা প্রাণী হবে যাকে ধরে তার গলা বা মজ্জাস্থি (marrow) তে যবেহ করা সম্ভব হবে না। যদি তা সম্ভব হয় তা হলে তা অবশ্যই নির্দিষ্ট নিয়মে যবেহ করতে হবে, তা না করা হলে হালাল হবে না।
যদি তীর নিক্ষেপ করা বা শিক্ষাপ্রাপ্ত কুকুরের দ্বারা শিকার করা না হয়, আর তা এমন অবস্থায় হস্তগত হয় যে, তার মধ্যে এখনও জীবনের স্থিতি রয়েছে তা হলে প্রচলিত নিয়মে গলদেশে যবেহ করতে হবে। কিন্তু যদি তা স্থিতিশীল জীবন নেই, এমন অবস্থায় হস্তগত হয় তাহলে সেটি যবেহ না করাই সঙ্গত। আর যদি তার সেই অবস্থায় সেটিকে মৃত্যুর জন্যে ছেড়ে দেয়া হয়, তাহলে কোন গুনাহ হবে না। বুখারী ও মুসলিম এ হাদীস উদ্বৃত হয়েছে :
(আরবী*****************)
তুমি যখন তোমার শিকারী কুকুর পাঠাবে তখনই তার ওপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করবে। পরে তা যদি শিকারকে তোমার জন্যে আটকে রাখে আর তুমি সেটি জীবন্ত অবস্থায় হাতে পাও তাহলে তুমি যবেহ করবে।
শিকার করার উপায়
যে সব উপায়ে শিকার করা যায় তা দুধরনের :
১. তীক্ষ্ণ শানিত অস্ত্র, যেমন তলোয়ার, বল্লম ইত্যাদি। কুরআনের আয়াতে এ দিকের ইঙ্গিত পাওয়া যায় :
(আরবী********)
তা পায় তোমাদের হস্ত এবং তীরসমূহ। (সূরা মায়িদা : ৯৪)
২. শিকারী জন্তু, যাকে শিকার কার্যের জন্যে রীতিমত শিক্ষিত ও ট্রেনিং প্রাপ্ত করা হয়েছে, যেমন কুকুর, বাজ ইত্যাদি। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে : (আরবী******************)
তোমাদের জন্যে হালাল করা হয়েছে সব পাক-পবিত্র জিনিস, আর তোমাদের যেসব শিকারী জন্তু ট্রেনিং প্রদত্ত, আল্লাহ তোমাদের যা শিখিয়েছেন তা দিয়ে তোমরাও শিক্ষিত করে তোল.........। (সূরা মায়িদা : ৪)
শানিত অস্ত্র দ্বারা শিকার করা
অস্ত্র দ্বারা শিকার করানোর দুটি শর্ত রয়েছে :
প্রথম, অস্ত্রটি শিকারের দেহের মধ্যে এমনভাবে বিদ্ধ হয়ে যাবে যে, এই জখমই সেটির মৃত্যুর কারণ হবে। অস্ত্রের চাপে পড়ে যেন মৃত্যু না হয়। হযরত আদী ইবনে হাতিম (রা) নবী করীম (সা) কে জিজ্ঞাসা করলেন :
(আরবী***************)
আমি ফলা ছাড়া তীর দ্বারাই শিকার করি। আর তা লক্ষ্য ভেদ করে, সেটি খাওয়া কি জায়েয?
রাসূলে করীম (সা) জবাবে বললেন : (আরবী*******************)
যখন তুমি তীর নিক্ষেপ কর, তার ধারালো দিকটা যদি দেহে ঢুকে যায় তাহলে তা খাও। আর যদি পাশাপাশি লাগে ও তার আঘাতে মরে তাহলে তা খাবে না। (বুখারী, মুসলিম)
এ হাদীস থেকে জানা গেল, শিকরীর দেহে ঢুকে পড়াটাই আসল লক্ষ্য। যদি শিকারের মৃত্যু হয় ভারী বোঝার তলায় চাপা পড়ে তাহলে তা খাওয়া জায়েয হবে না। এ হিসেবে বন্দুক ও পিস্তল রিভালবারের গুলী দ্বারা শিকার করা জন্তু হালাল হবে। কোননা এই গুলী দেহভ্যন্তরে তীর, বল্লম, ও তরবারীর তুলনায়ও অধিক শানিত ও গভীরভাবে প্রবেশ করে। এ পর্যায়ে ইমাম আহমদ কর্তৃক উদ্বৃত একটি হাদীস হচ্ছে : (আরবী****************)
বন্দুক দ্বারা শিকার করা জন্তু বা পাখি খাবে না, তবে যবেহ করলে তা খেতে পার। আর বুখারী উদ্বৃত হযরত ইবনে উমর (রা) এর একটি উক্তিহচ্ছে : বন্দুক দ্বারা করা শিকার মওকযা লাঠির আঘাতে মরা জন্তুর মতোই হারাম, এতে বন্দোকা অর্থ মাটির ঢিলা। তা নিক্ষেপ করে শিকার করা জন্তু নিশ্চয়ই হারাম। কিন্তু এখানে বন্দুক বলতে আমরা আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র মনে করছি এবং তার দ্বারা শিকার করা জন্তু অবশ্যই হালার হবে।
বুন্দেকার সাথে সাদৃশ্য সম্পন্ন জিনিস হচ্ছে প্রস্তর খণ্ড বা পাকা ইটের টুকরা। নবী করীম (সা) বলেছেন :
(আরবী*********৯৮***********)
প্রস্তরখণ্ড বাইটের টুকরা দ্বারা শিকার কারা যায় না, শত্রুকেও গভীরভাবে যখম করা চলে না। তবে তাদ্দারা দাঁত ভাঙ্গা যায় ও চক্ষু ফোটান যায়। (বুখারী, মুসলিম)
দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, হাতিয়ার নিক্ষেপ করা বা অস্ত্র চালানর সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করতে হবে। নবী করীম (সা) হযরত আদী ইবনে হাতিম (রা) কে যেমন শিক্ষা দিয়েছেন। ও বিষয়ে তাঁর বর্ণনা করা হাদীসসমূহ বিশেষ গুরুত্বের অধিকারী।
কুকুর দ্বারা শিকার করা
কুকুর বা বাজ, শিকার ইত্যাদি দ্বারা যখন শিকার করতে চাওয়া হবে, তখন নিম্নোক্ত শর্তসমূহ পালন করতে হবে :
একটি হচ্ছে, জন্তু বা পাখিটিকে শিকার করার কাজটি রীতিমত শিক্ষা ও ট্রেনিং দিতে হবে।
দ্বিতীয় এই যে, শিক্ষাপ্রাপ্ত জন্তু বা পাখিটী তার মালিকের জন্যে শিকার করবে, নিজের খাওয়ার জন্যে নয়। কুরআনের ইঙ্গিত থেকে তাই বুঝতে পারা যায়।
আর তৃতীয় হচ্ছে, সেটিকে শিকারের উদ্দেশ্য পাঠানোর সময় সেটির উপর বিসমিল্লাহ বলে দিতে হবে।
নিম্নোদ্বৃত আয়াতে এ সব কটি শর্তের কথা বলে দেয়া হয়েছে :
(আরভী******************)
লোকেরা তোমার কাছে জিজ্ঞাস করে তাদের জন্যে কি কি হালাল করা হয়েছে? তুমি বল, তোমাদের জন্যে হালাল করা হয়েছে সব পাক-পবিত্র উত্কষ্ট দ্রব্য এবং যেসব শিকারী জন্তু বা পাখি তোমরা শিখিয়ে পড়িয়ে তৈয়ার করে নিয়েছ শিকার করার জন্যে- ওরা যা তোমাদের জন্যে আটকিয়ে রাখবে তা তোমরা খাও এবং তার ওপর তোমরা আল্লাহর নাম উচ্চারণ কর।
১. শিকারী জন্তু বা পাখি শিক্ষাদানের ব্যাপারটিও সুস্পষ্ট। তা হচ্ছে সেটির ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রন কার্যকর করা, নিজ আদেশ মতো সেটিকে পরিচালিত করতে পারা, যখন যেদিকে ইচ্ছা সেটিকে চালিত করতে পারা এবং সেটির সে অনুযায়ী কাজ করতে প্রস্তুত হওয়া। শিকার করে মালিকের কাছে উপস্থিত করতে অভ্যস্ত হওয়া, মালিকের অনুপস্থিতিতে তার জিনিসপত্রের রক্ষণাবেক্ষণ। করা। মালিক সেটিকে তাড়ালে তাড়িত হওয়া। এ সব শর্ত আরোপের ব্যাপারে কোন কোন ফিকাহবিদের কিছুটা দ্বিমত আছে বটে, কিন্তু মোট কথা হলো, প্রচলিত নিয়মে শিকারী জন্তু বা পাখিকে সুশিক্ষিত করে তুলতে হবে।
২. মালিকের জন্যে শিকার রক্ষা করার অর্থ, শিকারী জন্তু বা পাখি শিকারটিকে নিজে খাবে না, মালিকের জন্যে রেখে দেবে। নবী করীম (সা) বলেছেন : (আরবী*******************)
তুমি যখন শিকার করার উদ্দেশ্যে কুকুর প্রেরণ কর, তখন সে শিকার করে তা থেকে যদি কিছু খায়, তাহলে তুমি তা খাবে না। কেননা প্রমাণিত হয়েছে যে, সেটি শিকারকে নিজের জন্যেই ধরে রেখেছে। আর পাঠানর পর শিকার করে যদি নিজে না খায়, তাহলে তুমি তা খেতে পার। কেননা প্রমাণিত হয়েছে যে, সেটি তার মালিকের জন্যে শিকারকে ধরে রেখেছে। (আহমদ)
কোন কোন ফিকাহবিদ শিকারী জন্তু – কুকুর ও শিকারী পাখি যেমন বাজ শিকরার মধ্যে পার্থক্য করেছেন। বলেছেন, শিকারী পাখি যদি শিকার থেকে কিছু খায়ও তবু তা খাওয়া মুবাহ। কিন্তু কুকুর খেলে তা খাওয়া যায়েয নয়।
এই দুটি শর্তে যথেষ্ট যৌক্তিকতা রয়েছে। কুকুরকে শিকার কার্যের জন্যে শিক্ষিত করে তোলা ও তার শিকার করে শিকারটিকে মালিকের জন্যে ধরে রাখা মানুষের উচ্চ মর্যাদার সথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কুকুরের উচ্ছিষ্ট খাবার থেকে মানুষকে দূরে রাখার উদ্দেশ্যেই এ শর্ত আরোপ করা হয়েছে। কেননা কুকুর শিক্ষাপ্রাপ্ত হলে ও শিকার করে সেটিকে মালিকের জন্যে ধরে রাখলে সেটি এক শিকার যন্ত্র মাত্র, শিকারী শিকার কাজে ব্যবহার করেছে। যেমন শিকারী তীর বল্লম বা বন্দুক চলিয়ে থাকে।
৩. কুকুর পাঠানর সময় বিসমিল্লাহ বলাটা তীর নিক্ষেপ বা বল্লম কিংবা ছুরি চালান করে বিসমিল্লাহ বলার মতোই। কুরআনের আয়াতে তারই নির্দেশ দেয়া হয়েছে : (আরবী*******************)
৪. এ বিষয়ে বহু সহীহ হাদীসও বর্ণিত হয়েছে, যেমন হযরত আদী ইবনে হাতিম (রা) বর্ণিত হাদীসমূহ।
উপরিউক্ত শর্ত থেকে একথাও সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে, প্রেরিত কুকুরটির সাথে অপর কোন কুকুর শরীক হলে এ দুয়ের শিকার খাওয়া হালাল হবে না। হযরত আদী (রা) জিজ্ঞাস করলেন :
(আরবী******************)
আমি আমার কুকুর শিকারের জন্যে পাঠাই, পরে সেটির সঙ্গে দ্বিতীয় একটি অপরিচিত কুকুরও দেখতে পাই, তখন কি করব?
নবী করীম (সা) বললেন : (আরবী***************)
তাহলে তুমি শিকার খাবে না। কেননা তুমি তো বিসমিল্লাহ বলেছ তোমার নিজের প্রেরিত কুকুরটির উপর, অপরটির ওপর নয়। (আর তুমি জান না এ দুটির মধ্যে কোনটি শিকার করেছে?)
তীর নিক্ষেপ করা বা শিকার পাঠানর সময় বিসমিল্লাহ বলতে যদি ভুলে যায়, তাহলে খাওয়ার সময় এই ভুল শুধরে নিলেই চলবে। আল্লাহ দয়া করে মসলিম উম্মতের অনেক ভুল-ভ্রান্তিই মাফ করে দিয়েছেন এবং দেন। এটাই সেই পর্যায়ের গণ্য।
তীর নিক্ষেপের পর শিকার মৃতাবস্থায় পাওয়া
এ রকমটা প্রায় ঘটে ও ঘটতে পারে যে, শিকারী শিকারের উদ্দেশ্যে তীর নিক্ষেপ করল, তা শিকারকে বিদ্ধ করল, পরেতা চোখের আড়ালে পড়ে যায়, হারিয়ে যায়। কিছু সময় পর সেটি মৃত্যু অবস্থায় পাওয়া যায়- কয়েকদিন পর পাওয়ার ঘটনাও বিরল নয়। এরূপ অবস্থায় কয়েকটি শর্তে শিকারটি হালাল হতে পারে :
১. সেটি যেন পানিতে পড়ে না থাকে। এ পর্যায়ে হাদীস হচ্ছে : রাসূলে করীম (সা) বলেছেন :
(আরবী***********)
তুমি যখন তোমার তীর নিক্ষেপ করলে শিকারকে লক্ষ্য করে তখন সেটি পাও নিহত অবস্থায়, তাহলে তুমি সেটি খাও। তবে যদি সেটিকে পানিতে পড়া অবস্থায় দেখ, তাহলে খাবে না। কেননা শিকারটি তোমার তীরের আঘাতে মরেছে না পানিতে ডুবে মরেছে, তা তুমি জান না।
২. অপর কোন তীরের চিহ্ন তার উপর থাকবে না, যার ফলে জানা যেতে পারে যে, অপর কোন তীরই তার মৃত্যুর কারণ হয়নি। হযরত আদী ইবনে হাতিম (রা) বললেন : (আরবী********************)
ইয়া রাসূল! আমি তো শিকার করার জন্যে তীর নিক্ষেপ করি। পরের দিন সেটি আমি পাই, তার ওপর আমার তীর বিদ্ধ হয়ে আছে।
নবী করীম (সা) বললেন : (আরবী****************)
তুমি যদি নিশ্চিতভাবেই জানতে পার যে, তোমার নিক্ষিপ্ত তীরই ওটিকে মেরেছে এবং তার ওপর কোন হিংস্র জন্তুর কোন চিহ্ন না পাওয়া যায়, তাহলে তুমি তা খেতে পার। (তিরমিযী)
৩. শিকারটা যেন পচেঁ যাওয়ার উপক্রম না হয়। কেননা সুস্থ মানব প্রকৃতি পঁচা জিনিস খেতে ঘৃণা করে। তা ছাড়া তার ক্ষতিকর দিক তো রয়েছেই। মুসলিম শরীফে বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে : নবী করীম (সা) হযরত আবু সা‘লাবা (রা) কে বললেন :
(আরবী*****************)
তুমি তীর নিক্ষেপ করার পর তা যদি তিনটি দিন অদৃশ্য হয়ে থাকে এবং তার পর তুমি শিকারের খোঁজ পাও, তাহলে তা পঁচে না গেলে তুমি খেতে পার।
মদ্য
মদ্য বা সূরা বলা হয় এমন এক এ্যালকোহলীয় পদার্থকে, যা পান করা হলে নেশাগ্রস্ত হতে হয়।
এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা পর্যায়ে আমরা প্রথমেই বলতে চাই, এ পদার্থটি পান করার ফলে ব্যক্তির বিবেক-বুদ্ধি ও দৈহিক স্বাস্থ্যে মারাত্মক ক্ষতি সাধিত হয়। তার দ্বীনদারীও নি:শেষ হয়ে যায়। বৈষয়িকতার দিক দিয়েও তাকে কঠিন বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে যেতে হয়। তার পরিবারটিকেও বিরাট ক্ষতির মধ্যে পড়তে হয়। আর এরূপ অবস্থা জাতি ও সমাজের বস্তুগত, নৈতিক ও আধ্যত্মিক জীবনে চরম দুর্গতি নিয়ে আসে অনিবার্যভাবে।
একজন বিশেষজ্ঞ ঠিকই বলেছেন যে মানুষকে সুরা যতটা কঠিন আঘাত হেনেছে ততটা আর কিছুই নয়। দুনিয়ার হাসপাতালসমূহ করে দেখলে দেখা যাবে মদ্য পানের দরুণ বহু লোক পাগল হয়ে গেছে, চিকিত্সার করা যায় না এমন রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েছে। মন-মগজের সুস্থতা হারিয়ে ফেলে হত্যাকাণ্ড ঘটায়, স্নায়বিক রোগে জর্জরিত হয়ে থাকে, পেটে স্থায়ী রোগ সৃষ্টি হয়। এমনকি অনেকে স্থীয় ধন-সম্পদ উড়িয়ে নি:স্ব সর্বস্ব হয়ে পড়ে। এদের সংখ্যা এত বেশি হবে যে, এদেরকে যত নসীহতই করা হোক, সবই বৃথা যাবে। এদের জীবনে কোনরূপ পরিবর্তন আনা সম্ভবপর হবে না।
জাহিলিয়াতের যুগে আরবরা সুরা পানের জন্যে পাগল হয়ে গিয়েছিলে। তাদেরও সুরা আসক্তির কোন সীমা ছিল না। তাদের ভাষায় সুরার প্রায় একশটি নাম রাখা হয়েছিল। তাদের কাব্য ও কবিতায় সুরার বিভিন্ন প্রকারের উল্লেখ রয়েছে, প্রত্যেক প্রকারের বিশেষত্ব বর্ণনা করা হয়েছে। তা পান ও পরিবেশনকরী-কারিণীদের সৌন্দর্য বর্ণনায়, সুরা পানের মজলিস সমূহের গুণগানের মুখর হয়ে উঠেছিল।
ইসলাম এসে তাদেরকে একটা সুনির্দিষ্ট ও সুস্থ পথে শিক্ষিত ও পরিচালিত করে। এজন্যে মদ্যপান হারামকরণের ক্রমিক নীতি অবলম্বিত হয়েছে।
সর্ব প্রথম নেশাগ্রস্থ হয়ে নামায পড়তে নিষেধ করা হয়। অতপর তাদের বোঝান হয় যে, মদ্যপানের গুনাহ তার কল্যাণের তুলনায় অনেক বেশি। আর শেষ পর্যায়ে সূরা আল মায়িদার ব্যাপক তাত্পর্যপূর্ণ আয়াতের মাধ্যমে মদ্যপানকে চিরদিনের তরে ও চূড়ান্তভাবে হারাম করা হয়। আয়াতটি এই : (আরবী*************************)
হে ঈমানদার লোকেরা, নিশ্চিতভাবে জানবে, মদ্য, জুয়া, বলিদাদের নির্দিষ্ট স্থান এবং ভাগ্য জানার নিয়ম নিতান্তই অপবিত্র শয়তানী তত্পরতা মাত্র। অতএব তোমরা তা পরিহার কর। আশা করা যায়, তোমরা সাফল্য লাভ করতে পারবে। এ মদ্য ও জায়ার মধ্যে তোমাদের নিক্ষেপ করে শয়তান তোমাদের পরস্পরে শত্রুতা ও হিংসা-দ্বেষ সৃষ্টি করে দেয়; আর আল্লাহর স্মরণ ও নামায থেকে তোমাদের বিরত রাখে। এমনতবস্থায় তোমরা এসব কাজ থেকে বিরত হবে কি?
এ আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ তা’আলা মদ্যপান ও জুয়া খেলাকে কঠোর ভাষায় হারাম করেছেন এবং তা পরিহার করার জন্যে অত্যন্ত কড়া আদেশ বা তাগিদ করেছেন। এ আয়াতে মদ্যপান ও জুয়া খেলাকে বলিদানের স্থান ও ভাগ্য জানার উপায়াবলীর সঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে এ দুটির জঘন্যতা ও বীভত্সতা দেখাবার জন্যে। এ কাজকে কুরআনী ভাষায় رجس বলা হয়েছে এবং এটাকে শয়তানের কাজ বলা হয়েছে। আর শয়তানী কাজ যে জঘন্য রকমের নির্লজ্জতা তা বলাই বাহুল্য। এভাবে আয়াতে এ দুটিকে পরিহার করতে বলা হয়েছে। আর এ দুটোকে সামষ্টিক ক্ষতির দিক ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে যে, এর ফলে মদ্যপায়ী নামায পড়তে পারবে না, আল্লাহকে ভুলে যাবে। লোকদের পরস্পরের মধ্যে চরম হিংসা-বিদ্বেষ ও প্রাণের শত্রুতা পর্যন্ত সৃষ্টি হয়ে পড়বে। নাময পড়া ও আল্লাহকে স্মরণ করা- এ দুটো আত্মিক উত্কর্ষ লাভের মাধ্যমে মানুষ হারিয়ে ফেলবে। এসব বলার পর ঈমানদার লোকেরা সে দুটির কাজ সম্পূর্ণ পরিহার করে চলবে কিনা, তা অত্যন্ত কড়া ভাষায় জানতে চাওয়া হয়েছে।
এরূপ কড়া আদেশ ও নির্দেশের জবাবে মুমিনদের একটি মাত্র কথাই বলার থাকতে পারে। আর তা হচ্ছে :
হে খোদা ! আমরা পরিহার করলাম।
হে খোদা আমরা তা থেকে বিরত থাকলাম।
আর কার্যত মুসলিম বিস্ময়কর দৃশ্যের সৃষ্টি করল। কিছু সংখ্যক মুসলিম একস্থানে একত্রিত হয়ে মদ্যপান করছিল। কারো হাতে পাত্র ছিল কিছু পান করেছে, এখনও পাত্র শেষ হয়নি। এ আয়াত শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গেই সে পাত্রটি মুখের কাছ থেকে টেনে নিল এবং অবশিষ্ট অংশ উপুড় করে ফেলে দিল।
মদ্য পানের এ দুষ্ক্রিয়া যা ব্যক্তি পরিবার সমাজ জাতি ও রাষ্ট্রের জীবন কঠিনভাবে প্রতিফলিত হয়, আধুনিক কালেরও বহু কয়টি রাষ্ট্র আইন ও ক্ষমতার বলে তা নিষিদ্ধকরণের জন্যে চেষ্টা চালিয়েছে। আমেরিকা এক সময় আইনের জোরে মদ্যপান বন্ধ করতে চেয়েছিল। কিন্তু এ কাজ চরমভাবে ব্যর্থতা স্বীকার করতে হয়। কেবলমাত্র ইসলামই মদ্যপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তার মূলোত্পাটনে পূর্ণমাত্রায় সাফল্য লাভ করতে সক্ষম হয়েছে।
গীর্জা-কর্তৃপক্ষের মধ্যে সূরা পান সম্পর্কে খ্রিষ্টীয় ধর্মমত নির্ধারণে বড় মতদ্বৈততা দেখা দিয়েছে। তারা ইনজিলের এক একটি বাক্যাংশকে ভিত্তি করে একটা মত দাঁড় করিয়েছে :
অল্প পরিমাণ সুরা পান পাকস্থলীর জন্যে ভাল উপকারী।
এ কথা যদি নির্ভুল হয় আর মদ্য পাকস্থলীর জন্যে ভালই হয়, তাহলে অল্প পরিমাণ পান করত করতে মদ্যপায়ী বেশি বেশি পরিমাণে পান করতে শুরু করে দেবে, এটা তো অবধারিত। মদের একটি পাত্র আরও বহু কয়টি পাত্রের কামনা জাগিয়ে দেয় মাত্র। ফলে মাদ্যপান সে যেমন অভ্যস্থ হয়ে পড়বে, তেমনি পরিমাণের কোন সীমা রক্ষা করাই তার পক্ষে সম্ভব হবে না।
কিন্তু এ ক্ষেত্রেও ইসলামের ভুমিকা সুস্পষ্ট এবং অকাট্য। তার মতো শুধু মদ পানই হারাম নয়, সে কাজ সর্বপ্রকার সাহায্য-সহযোগিতাও সম্পূর্ণরূপে হারাম।
সমস্ত মাদক দ্রব্যই হারাম
নবী করীম (সা) যখন সর্বপ্রথম মদ্যপান নিষেধ ঘোষণা করেন তখন তিনি কি দিয়ে সুরা তৈরী করা হয়, সেদিকে আদৌ ভ্রুক্ষেপ করেন নি। তার নযর নিবদ্ধ ছিল তার ফল ও প্রতিক্রিয়ার উপর। আর তা হচ্ছে মাদকতা। কাজেই যে জিনিসেই মাদকতা থাকবে, তাই হারাম বিবেচিত হবে, তা সে বস্তু থেকেই তৈরী হোক- না কেন। মদ্য সম্পর্কে এ হচ্ছে ইসলামের চূড়ান্ত কথা। অতএব Beer এবং তার মতো অন্যান্য সর্বপ্রকার মাদক পানীয়ই সম্পূর্ণ হারাম।
নবী করীম (সা) এর কাছে মধু, ভুট্টা ও যব থেকে তৈরী মদ্য সম্পর্কে জিজ্ঞাস করা হয়েছিল। জবাবে তিনি একটি মৌলনীতির ঘোষনা করেন এবং বলেন : (আরবী*********************)
সকল প্রকার মাদক দ্রব্যই খামর। আর সব খামরই হারাম। (মুসলিম)
হযরত উমর ফারূক (রা) নবী করীম (সা) এর মিম্বারের ওপর দাঁড়িয়ে ঘোষনা করেছিলেন :
(আরবী************)
যে দ্রব্যই মানুষের বিবেক-বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন ও বিকৃত করে, তাই খামর এবং নিষিদ্ধ। (বুখারী, মুসলিম )
মাদক দ্রব্য মাত্রই হারাম- অল্প হোক কি বেশি
ইসলামে মাদক দ্রব্য মাত্রই হারাম ঘোষিত হয়েছে। এ ব্যাপারে তার পরিমাণের ওপর মোটেই দৃষ্টি দেয়া হয়ানি। কাজেই তার পরিমাণ কম হোক কি বেশি, উভয় অবস্থায়ই তা হারাম। এ পিচ্ছিল পথে পা দিয়ে মানুষ যেন আছাড়ের পর আছাড় খেতে বাধ্য না হয়, সে জন্যেই এ ব্যবস্থা। নবী করীম (সা) স্পষ্ট করে বলেছেন :
(আাবী****************)
যে জিনিসের অধিক পরিমাণ নেশাগ্রস্ত করে, তার অঞ্জলী ভরা পরিমাণও হারাম। (আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিযী)
(আরবী*******************)
যে জিনিসের কয়েক রতি পরিমাণও নেশাগ্রস্ত করে, তার অঞ্জলী ভরা পরিমাণও হারাম।
সুরার ব্যবসা
নবী করীম (সা) সুরা কম কি বেশি পরিমাণ পান করাকেই শুধু হারাম করে ক্ষান্ত হন নি। সুরার ব্যবসা করাকেও তিনি হারাম ঘোষণা করেছেন। এমনকি, অমুসলিমদের সাথেও এ ব্যবসা জায়েয নয়। কাজেই সুরার আমদানী বা রফতানী পর্যায়ের ব্যবসা করা কোন মুসলমানদের জন্যেই জায়েয হতে পারে না। সুরা উত্পাদনের কারখানা নির্মাণ বা বার খুলে বসা- কোনটিই জায়েয নয়। সুরার দোকানে চাকরী করাও সমানভাবে নিষিদ্ধ। এ কারণেই নবী করীম (সা) সুরার ব্যাপারে দশ ব্যক্তির ওপর অভিশাপ বর্ষণ করেছেন। তারা হচ্ছে :(আরবী**********************)
সুরা উত্পাদনকারী, যে, উত্পাদন করায়, মদ্যপায়ী, বহনকারী, যার কাছে বহন করে নেয়া হয়, যে পান করায় পরিবেশনকারী, বিক্রয়কারী, মূল্য গ্রহণ ও ভক্ষণকারী, ক্রয়কারী এবং যার জন্যে তা ক্রয় করা হয়- এ সকলেরই ওপর অভিশাপ। (তিরমিযী, ইবনে মাযাহ)
(আরবী*******************)
আল্লাহ তাআলা সুরা পান হারাম করেছেন। কাজেই যে ই এ হুকুম জানতে পারবে তার কাছে তার কিছু পরিমাণ থাকলেও তা পানও করতে পারবে না, তা বিক্রয়ও করবে না। (মুসলিম)
হাদীস বর্ণনা কারী বলেন, এ সময় যার কাছে সূরা মজুদ ছিল। তারা সকলেই তা মদীনার পথে ঘাটে প্রবাহিত করে দিয়েছিলেন।
সুরা পানের সব পথ বন্ধ করার উদ্দেশ্যে ঘোষণা করা হয়েছে, কোন মুসলমান যেন এমন কোন ব্যক্তির কাছে আঙ্গুর বিক্রয় না করে, যার সম্পর্কে জানা যাবে সে, সে আঙ্গুর দ্বারা সুরা তৈয়ার করবে।
হাদীসে বলা হয়েছে : (আরবী************************)
যে লোক আঙ্গুরের ফসল কেটে রাখাই করবে কোন ইয়াহুদী, খ্রিস্টান বা এমন ব্যক্তির কাছে বিক্রয় করার উদ্দেশ্যে যে তা থেকে সুরা তৈরী করবে, তাহলে সে জেনে-শুনেই আগুনে ঝাপ দিল। (আল তিবরানী ফিল আওসাত)
মুসলমান সুরা উপঢৌকন দিতে পারে না
সুরা বিক্রয় করা ও তার মূল্য ভক্ষন করাই মুসলমানদের জন্যে হারাম নয়, কোন মুসলিম ব্যক্তিই তা কোন অমুসলিমকে উপঢৌকন স্বারূপ দেয়াও সম্পূর্ণ হারাম। তার জন্যেও এ উপঢৌকন আসতে পারে না। কেননা মুসলমান পবিত্র। সে পবিত্র জিনিস ছাড়া অন্য কিছু উপঢৌকন বা মেহমানী হিসেবে কাউকে দিতেও পারেনা সে নিজেও গ্রহণ করতে পারে না। এক ব্যক্তি রাসূলে করীমের খেদমতে হাদিয়া হিসেবে সুরা পেশ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল। নবী করীম (সা) তা জানতে পেরে তাকে বললেন যে, আল্লাহ তাআলা সুরা হারাম করেছেন। তখন লোকটি বলল : তাহলে আমি তা বিক্রয় করে দিই? রাসূল বললেন : (আরবী***********)
যিনি তা পান করা হারাম করেছেন তিনিই তা কোন ইয়াহুদীকে তোহফাস্বরূপ দেয়াও হারাম করেছেন।
তখন লোকটি বলল, তাহলে আমি তা নিয়ে কি করব? রাসূলে করীম (সা) বললেন : মদীনার অলিগলিতে তা প্রবাহিত কর।
সুরা পানের আসর পরিহার করা
এ প্রেক্ষিতেই মুসলিম মাত্রকেই সুরা পানের আসর বা মজলিস পরিহার করে চলবার জন্যে আদেশ করা হয়েছে। মদ্যপায়ীদের সঙ্গে উঠা বসা করাও তাদের জন্যে নিষেধ। হযরত উমর (রা) বর্ণনা করেছেন : হযরত রাসূলে করীম (সা) ইরশাদ করেছেন : (আরবী**********************)
আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমানদার ব্যক্তি যেন এমন মজলিসে বা টেবিলে একত্রে না বসে, যেখানে সুরা পরিবেশন করা হয়। (আহম্মদ)
অপরদিকে মুসলিম মাত্রেই কর্তব্য অন্যায় ও পাপকর্য বন্ধ করার জন্যে চেষ্টা করা। কিন্তু তা করা যদি সম্ভবই না হয়, তাহলে সে নিজে তো অন্তত সেখানে থেকে কেটে পড়বে।
হযরত উমর ইবনে আব্দুল আজীজ মদ্যপায়ীদের সঙ্গে সঙ্গে সে লোকদেরও দোররা মারতেন, যারা তাদের মজলিসে উঠা বসা করত- নিজেরা তা পান না করলেও। একবার কতিপয় মদ্যপায়ী ধরে আনা হলো। তিনি তাদের শাস্তি দেবার নির্দেশ দিলেন। কেউ বললেন , তাহলে তো ওকেই প্রথম শাস্তি দিতে হবে। তোমরা কি আল্লাহর ও ফরমান শুনতে পাওনি :
(আরবী******)
তোমাদের কুরআনে এ ফরমান নাযিল হয়েছে যে, তোমরা যখন আল্লাহর আয়াত অস্বীকার করতে ও তার প্রতি ঠাট্রা-বিদ্রুপ করা কথাবর্তা শুনতে পাবে, তখন তোমরা তার সাথে আর বসবে না। পরে যদি তারা অন্য কোন কথায় মনোযোগ দেয়, তখন অবশ্য অন্য কথা। কিন্তু ঐ সময়ও যদি তোমরা তাদের সাথে বসা থাক, তাহলে তোমরাও অনুরূপ অপরাধে অপরাধী হবে।
সুরা রোগ- ঔষধ নয়
এসব অকাট্য দলিল- প্রমাণের ভিত্তিতে বোঝা যায়, ইসলাম সুরা বিরোধী সংগ্রামে অত্যন্ত কঠিন ও অনমনীয় ভূমিকা গ্রহণ করেছে। মুসলিমকে তা থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চেয়েছে। মুসলমান ও সুরা পানের মাঝে দুর্লংঘ্য প্রাচীর দাঁড় করাতে চেয়েছে। যেন একটি ক্ষুদ্র ছিদ্র ও পথও উন্মুক্ত না থাকে। সুরাকে কোন কাজে ব্যবহার করার কোন সুযোগই মুসলমানদের জন্যে উন্মুক্ত রাখা হয়নি।
মুসলমানের জন্য মদ্যপান- সামান্য পরিমাণও জায়েয রাখা হয়নি। তা ক্রয়-বিক্রয়ও করা যেতে পারে না। হাদিয়া-তোহফা হিসেবে তা করো জন্যে পেশ করাও যেতে পারে না। তা তৈরী করাও নিষেধ, স্বীয় দোকানে, অফিসে বা বসবাসের ঘরে তা রাখাও সম্পূর্ণ হারাম। উত্সব-দাওয়াত-যিয়াফত-মেহমানদারীতে তা পেশ করা যেতে পারে না। অমুসলিম মেহমানদের মেহমানদারীও করা যেতে পারে না তা দিয়ে। অনুরূপভাবে খাদ্য পানীয়ের সাথে তা মিলিয়ে দেয়ারও কোন অনুমতি নেই ইসলামে।
তবে ঔষধ হিসেবে সুরা ব্যবহার করা যায় কিনা- আজকের মানুষের এ একটা প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাসূলে করীম (সা) কেও এ প্রশ্ন করা হয়েছিল। জবাবে তিনি বললেন : (আরবী*******************)
সুরা কোন ঔষধ নয় আসলে তা ব্যাধি মাত্র । (মুসলিম, আহম্মদ, আবূ দাউদ, তিরমিযী)
রাসূলে করীম (সা) বলেছেন : (আরবী*********************)
আল্লাহ রোগ-ব্যাধি ও তার ঔষধ উভয়ই নাযিল করেছে। তোমাদের রোগের চিকিত্সার ব্যবস্থাও তিনি করে দিয়েছেন। অতএব তোমরা চিকিত্সা করবে, তবে হারাম জিনিস দ্বারা নয়। (আবু দাউদ)
(আরবী*******************)
যে সব জিনিস তোমাদের জন্যে হারাম করা হয়েছে, আল্লাহ তাতে তোমাদের রোগের আরোগ্য রাখেন নি।
সুরা ও অন্যন্য হারাম দ্রব্য দ্বারা চিকিত্সা করান নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। এটা কোন বিস্ময়োদ্দিপক ব্যাপার নয়। কেননা একটি জিনিস হারাম করার অর্থ হচ্ছে তা থেকে দূরে থাকতে বলা, তা সম্পূর্ণ ও সর্বতোভাবে পরিহার করে চলতে নির্দেশ দেয়া। এক্ষণে তাই যদি ঔষধ হিসেবে ব্যবহার করা হয়, তাহলে সে হারাম জিনিসের মধ্যেই ডুবে থাকতে হবে, তার দিকেই উত্সাহ যোগান হবে। আর তাহলে সে জিনিস হারাম করাটাই অর্থহীন হয়ে যায়। ইমাম ইবনুল কাইয়্যেম এ যুক্তিই দেখিয়েছেন।
তিনি আরও বলেছেন : হারাম জিনিস ঔষধ হিসেবে ব্যবহার করার অনুমতি থাকলে তার প্রতি মানুষের আগ্রহ ও আকর্ষণই বৃদ্ধি পাবে। কেননা তার প্রতি মনের একটা স্বাভাবিক প্রবণতা রয়েছে। বিশেষ করে তা যখন উপকারী প্রমাণিত হবে, রোগ নিরাময়কারী ও স্বাস্থ্যদানকারী মনে হবে, তখন তা থেকে বিরত থাকা সম্ভব হবে না। সুরাকে ঔষধ হিসেবে ব্যবহার করার অনুমতি থাকলে তা লালসা চরিতার্থ করার উপায় হয়ে দাঁড়াবে। এ পর্যায়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ মানস্তত্ত্বিক দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে ইমাম ইবনুল কাইয়্যেম লিখেছেন :
ঔষধ দ্বারা আরোগ্য লাভের জন্যে তা আগ্রহ ও আন্তরিকতা সহকারে ব্যবহার করা কর্তব্য। তাকে উপকারী মনে করতে হবে। আল্লাহ তাতে যে আরোগ্য রেখেছেন তার বরকত লাভ সম্ভব হবে বলে মনে করতে হবে বলে মনে করতে হবে। কিন্তু একজন মুসলমান বিশ্বাস করে যে, সুরা অকাট্যভাবে হারাম। এ বিশ্বাসের কারণেই তার পক্ষে সুরার দ্বারা আরোগ্য লাভ সম্ভব হবে না। এরূপ বিশ্বাস সুরা সম্পর্কে ভাল ধারণার সৃষ্টি হতে দেবে না। তা আগ্রহ সহকারে গ্রহণ করাও কঠিন। বরং বান্দা ইমানে যতটা পরিপাক হবে, সুরাকে সে তত বেশি ঘৃণাই করবে। তাকে খারাপ মনে করবে, তা সে সহ্যই করতে পারবে না। এরূপ অবস্থায় সুরা ব্যবহারে রোগমুক্তি লাভ সম্ভব হবে না বরং তাতে তার রোগ বেড়েই যাবে। (আরবী*******************)
এ সব কথাই সত্য। তবুও প্রয়োজন ও ঠেকা-বাধাও শরীয়তের দৃষ্টিতে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। এ জন্যে তার প্রতি লক্ষ্য রেখে শরীয়তের বিধান রচনা করা হয়েছে। যে রোগে মানুষের জীবন বিপন্ন হয়ে পড়ে আর তার জন্যে সুরা বা সুরা মিশ্রিত কোন ঔষধ যদি একমাত্র ঔষধ রূপে চিহ্নিত করা হয়, তা ছাড়া যদি এমন আর কোন ঔষধই পাওয়া না যায় তার বিকল্প হতে পারে কোন ইমানদার মুসলিম ডাক্তারই যদি তার ব্যবস্থা দিয়ে থাকে যার মধ্যে ঈমানী বলিষ্ঠতা বর্তমান, কেবলমাত্র এরূপ অবস্থায়ই তা ঔষধ হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। (তবে এরূপ অবস্থা খুব যে দেখা যায় তা নয়) কেননা শরীয়ত মানুষের জীবন সহজতা নিয়ে আসে, প্রতিবন্ধকতা ও অসুবিধা দূর করে। অবশ্য ইসলামের এ অনুমতি নির্দিষ্ট ও সংকীর্ণ সীমার মধ্যেই কাজে লাগাতে হবে, তা লংঘন করা যাবে না। আল্লাহ তো বলেই দিয়েছেন : (আরবী*******************)
কেউ যদি কঠিনভাবে ঠেকায় পড়ে যায় কিন্তু সে নিজে ইচ্ছুক ও আগ্রহী নয়, সীমালংঘনকারীও নয়, তাহলে আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াবান।
চেতানা নাশক দ্রব্যাদি
খামর তাই যা মানুষের বিবেক-বুদ্ধি আচ্ছন্ন করে দেয়। এ একটি অতী গুরুত্বপূর্ণ ও ব্যাপক তাত্পর্যপূর্ণ মৌলনীতি। হযরত উমর (রা) রাসূলে করীমের মিম্বরে দাঁড়িয়ে ভাষণ দান প্রসঙ্গে ঘোষণা করেছিলেন। এ কথার আলোকে কুরআনে ব্যবহৃত خمر শব্দের তাত্পর্য বোঝা যায় এবং এ ব্যাপারে কোনরূপ শোবাহ-সন্দেহের অবকাশ থাকে না। এ থেকে অকাট্যভাবে জানা গেল, যে দ্রব্যই মানুষের বিবেক-বুদ্ধি আচ্ছন্ন করে, অনুভূতি ও বিচার-বুদ্ধি, বোধশক্তি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ শক্তি হরণ বা কোন রূপ প্রভাবিত করে, তাই খামর বা সুরা (মদ্য) নামে অভিহিত। আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সে জিনিসকেই চিরদিনের তরে হারাম করেছেন।
গাঁজা, আফিম, কোকেন, প্রভৃতি এই পর্যায়েরই জিনিস। তা মানুষের বিবেক-বুদ্ধিকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করে দেয় যে, দুরবর্তী জিনিস নিকটবর্তী এবং নিকটবর্তী জিনিস দূরবর্তী মনে হয়। যা বস্তবিকই বর্তমান, সে ব্যাপারে বিভ্রম বা ভ্রান্তি হতে শুরু করে। আর যা প্রকৃতপক্ষেই নেই, তা আছে বলে মনে করতে থাকে। এভাবে সে চরম ভুল-ভ্রন্তি ও ভিত্তিহীন ধারণা-কল্পনার সমুদ্রে হাবুডুবু খেতে থাকে। শেষ পর্যন্ত সে নিজের সত্তা নিজের দীন ধর্ম ও দুনিয়া সব কিছুই ভুলে গিয়ে নিছক কল্পনার জগতে বিচরণ করতে শুরু করে।
তা ছাড়া এ ধরনের মাদক দ্রব্য পানে স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ে। স্নায়ুবন্ডলী চেতনা হারিয়ে ফেলে। শরীর দুর্বল হয়ে যায়। উপরন্তু তার দুর্বলসম মানসিকতা, সাহসহীনতা, নৈতিক পতন ও ইচ্ছাশক্তি ধৈর্যহীনতার সৃষ্টি হয়, তার ফলে এসব বিষাক্ত দ্রব্যাদি পানে অভ্যস্ত ব্যক্তি সমাজ দেহে ব্যাপক পচন ধরিয়ে দেয়।
এতসব দোষ ও বিপর্যয় চাড়াও ধন-মালের অপচয় এবং ঘর-সংসারের ভাঙন ও বিপর্যয় এক অনিবার্য পরিণতি। অনেক সময় এসব চেতনা নাশক (annesthetic) দ্রব্যাদি পানে অভ্যস্ত ব্যক্তি তার সন্তান-সন্ততির খাবার –দাবারের পয়সাও এই দ্রব্য ক্রয়ে ব্যয় করে ফেলে। এ জন্য দুর্নীতি ও অসত্ পন্থা অবলম্বনেও তাদের কোন কন্ঠা বা দ্বিধা থাকে না।
পূর্বেই বলা হয়েছে, ইসলামের মৌলনীতি হচ্ছে, হারাম জিনিস সমূহই সর্ব প্রকার জঘন্যতা, মন্দত্ব, নিকৃষ্টতা ও ক্ষতির কারণ। আর বাস্তবত এ সত্য উদঘাটিত হয়েছে যে, স্বাস্থ্যের দৃষ্টিতে মনস্তাত্ত্বিক, সামষ্টিক ও অর্থনৈতিক দৃষ্টিতেও এ সব জিনিসই অত্যান্ত ক্ষতিকর ও মারাত্বক- এতে কোনই সন্দেহ নেই। যে সব ফিকাহবীদ জীবনদ্দশায় এ সব জিনিসের প্রচলন শুরু হয়েছিল, তারা এগুলোর জঘন্যতা ও নিকৃষ্টতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ একমত। শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া এদের মধ্যে সর্বাগ্রসর। তিনি লিখেছেন:
হাশীশ-গাঁজা হারাম। তাতে বেঁহুশী হোক আর নাই হোক। তা পান করলে হৃদয়-চাঞ্চন্য, উল্লাস-স্ফূর্তী এবং আনন্দে আত্মহারা ভাব জেগে উঠে। এ কারণে প্রধানত খোদাদ্রোহী লোকেরাই তা পান করতে অভ্যস্থ। ক্রিয়া ও বিশেষত্বের দিক দিয়ে তা সুরার মতই উত্তেজক। তা মানুষকে ঝগড়া-ঝাটি করতে উদ্বুদ্ধ করে। আর গাঁজা বুদ্ধিবিভ্রম ঘটিয়ে চরম জিল্লতির সৃষ্টি করে। তা মানুষের বিবেক ও মেজাজ প্রকৃতিও খারাপ করে দেয়। তা যৌন দুষ্প্রবৃত্তির উত্তেজনা সৃষ্টি করে। মানুষ আত্মমর্যাদাবোধও হারিয়ে ফেলে। এসব কারণে গাঁজা মাদকতার দিক দিয়ে সুরার চাইতেও বেশি নিকৃষ্ট ও অনিষ্টকর। তাতার সম্প্রদায়ের অভ্যুত্থানের প্রভাবে লোকেদের মধ্যে এ জিনিসের ব্যাপক প্রচলন ঘাটায়। তা পান করলে- পরিমাণ বেশি বা কম- মদ্যপানের দণ্ড আশি বা চল্লিশ চাবুক মারা উচিত।
যে ব্যক্তি গাঁজা পান করেছে বলে প্রমাণিত হবে, মনে করতে হবে সে সুরা পান করার অপরাধ করেছে। কোন কোন দিক দিয়ে তা সুরা পানের চাইতেও বেশি মাত্রায় অপরাধ। কাজেই তাকে সুরা পানের দণ্ডই দিতে হবে। শরীয়তের নিয়ম হলো যেসব হারাম জিনিসের প্রতি মনে কামনা ও বাসনা জাগে যেমন সুরা ও ব্যভিচার তাতে হদ্দ জারী করতে হবে। কিন্তু যেসব জিনিসের প্রতি কামনা জাগে না, যেমন মুর্দার খাওয়া, তা খেলে তাজীর দিতে হবে। আর গাঁজা পানকারীদের কাছে তা এতই প্রিয় ও লোভনীয় যে, তা তারা কখনই ত্যাগ করতে পারে না অথচ কুরআন ও সুন্নাতের অকাট্য দলিলাদি এগুলোর হারাম হওয়ার কথা এতই অকাট্যভাবে প্রমাণ করে যেমন সুরা ও অন্যান্য ধরনের জিনিস হারাম হওয়া প্রমান করে।
(আরবী**************)
ক্ষতিকর জিনিস মাত্রই হারাম
ইসলামী শরীয়তের সাধারন নিয়মে মুসলমানের পক্ষে এমন কোন জিনিস খাওয়া বা পান করা জায়েয নয়, যা তাকে সঙ্গে সঙ্গে অথবা ধীরে ধীরে ধ্বংস ও সংহার করতে পারে। সর্ব প্রকারের বিষ বা অপর কোন ক্ষতিকর জিনিস এ জন্যেই হারাম। খুব বেশি পরিমান পানাহার করাও নাজায়েয, কেননা তাতে রোগাক্রান্ত হয়ে পড়া স্বাভাবিক। মুসলিমকে কেবল নফসের দাবি পূরণের কাজ করলেই চলবে না, তার দ্বীন, মিল্লাত, জীবন, স্বাস্থ্য, ধন-মাল ও আল্লাহর অসংখ্য নিয়ামতও তার কছে আমানস্বরূপ রক্ষিত। সে সবের হকও আদায় করতে হবে। কাজেই এর কোন একটা জিনিসও বিনষ্ট করার তার কোন অধিকার নেই। স্বয়ং আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন : (আরবী**********************)
তোমরা নিজেদের সত্তাকে হত্যা কর না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি অতীব দয়াময়। (সূরা আন-নিসা : ২৯)
(আরভী*********************)
তোমরা নিজেদের হাতেই নিজেদেরকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষপ করবে না।
রাসূলে করীম (সা) বলেছেন : (আরবী********************)
নিজের ক্ষতি স্বীকার করবে না, অন্যকেও ক্ষতিগ্রস্ত করবে না।
এসব মৌল নীতিমালার ভিত্তিতে আমরা বলতে পারি, তামাক ব্যবহারকারীদের বক্ষে তা যদি ক্ষতিকর হয়, তাহলে তা হারাম। (হারাম বলার সরাসরি কোন দলিল নেই। যা আছে তাতে বড়জোর মাকরূহ বলা যায়) বিশেষ করে চিকিত্সক যদি কোন বিশেষ ব্যক্তির পক্ষে তামাক খাওয়া ক্ষতিকর বলে দেয়, তাহলে তা উপরিউদ্বৃত আয়াতে নিষিদ্ধ আর যদি তা স্বাস্থ্য হানিকর নাও হয়, তবু তাতে যে ধন মালের চরম অপচয় হয়, তাতে না কোন দ্বীনী ফায়দা আছে, না বৈষয়িক, এতে কোন সন্দেহ নেই। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে : (আরভী*************************)
ধন-মালের অপচয় বিনষ্ট করতে নবী করীম (সা) নিষেধ করেছন।
কিন্তু কেউ যদি এতদূর গরীব হয়ে থাকে, যার পক্ষে তার নিজে ও পরিবারবর্গের জন্যে প্রয়োজনীয় খরচ পত্র যোগাড় করাও কঠিন, তাহলে তার জন্যে এ নিষেধ অধিক কড়া ও তাগিদপূর্ণ।
পোশাক পরিচ্ছদ
মুসলমান আল্লাহর সৃষ্টি করা সৌন্দর্য পোশাক ও উত্তম পরিচ্ছদ ব্যবহার করে নিজের আকার-আকৃতি, ছবি-সুরত সৌন্দের্যমণ্ডিত করবে, ইসলামে তা শুধু জায়েযই নয়, তা পুরোপুরি কাম্যও বটে।
ইসলাম পোশাক দ্বারা দুটো লক্ষ্য অর্জন করতে চায়। একটি হচ্ছে লজ্জাস্থান আবৃতকরণ আর দ্বিতীয়টি সৌন্দর্য লাভ। আল্লাহ তাআলা জাতির জন্যে পরিচ্ছদ ও সৌন্দর্য সামগ্রীর সুব্যবস্থা করে বিরাট অনুগ্রহ করেছেন। তিনি নিজেই বলেছেন :
(আরবী*********************)
হে আদম সন্তান ! আমরা তোমাদের জন্যে পোশাক পরিচ্ছদ নাযিল করেছি যা তোমাদের লজ্জাস্থান আবৃত করে এবং তোমাদের ভূষণও। পোশাকের উদ্দেশ্যে লজ্জাস্থান আবৃতকরণ এবং ভূষণ- এ দুয়ের মধ্যে অবশ্যই সামঞ্জস্য ও ভারসাম্য স্থাপন ও রক্ষা করতে হবে। এ ভারসাম্য নষ্ট করা হলে ইসলামের রাজপথ পরিহার করে শয়তানী পথ অবলম্বন করা হবে। এ এক অতীব গুরুত্বপূর্ন তত্ত্ব। নিম্নোদ্বৃত আয়াতে আল্লাহ তাআলা শয়তানের পদাংক অনুসরণ করে নগ্নতা ও সৌন্দর্যহীনতার পথ অবলম্বন করতে সুস্পষ্ট ভাষায় নিষেধ করেছেন : (আরবী*********************)
হে আদম সন্তান! শয়তান যেন তোমাদের বিপদে নাফেলে, যেমন করে সে তোমাদের পিতামাতাকে জান্নাত থেকে বহিষ্কৃত করেছিল এবং তাদের পোশাক তাদের গাত্র থেকে খসিয়ে নিয়েছিল, যেন তাদের লজ্জাস্থানসমূহ তাদের সমুখে উন্মুক্ত করে দিতে পারে। (সুরা আল-আরাফ : ২৭)
অপর আয়াতে বলেছেন : (আরবী*********************)
হে আদম সন্তান! তোমরা তোমাদের সৌন্দর্য গ্রহণ কর প্রতিটি মসজিদের উপস্থিতিকালে এবং খাও, পান কর, কিন্তু সীমালংঘন করো না। (সূরা আল-আরাফ :৩১)
সুসভ্য মানুষ তার দেহের যেমন গোপন অঙ্গ উলঙ্গ করতে লজ্জাবোধ করে, তা আবৃত এবঙ ন্যাংটা পশুদের থেকে স্বতন্ত্র ছবি-সুরত গ্রহণ করাকে ইসলাম মুসলিম মাত্রের জন্যেই ফরয করে দিয়েছে। ইসলামের নির্দেশ হচ্ছে নির্জন একাকিত্বও লজ্জাস্থান আবৃত করে রাখবে, যেন লজ্জা-শরম মানুষের অভ্যাস ও স্বাভাবগত ভূষণে পরিণত হয়।
বহজ ইবনে হাকীম তাঁর দাদার সূত্রে বর্ণনা করেছেন : (আরবী*********************)
আমি বললাম, হে রাসূল ! আমরা আমাদের সতরের ব্যাপারে কতটা সতর্কতা অবলম্বন করব? আর কতটা নয়? রাসল বললেন, তোমার লজ্জাস্থানের সংরক্ষণ কর- নিজ স্ত্রী ও ক্রিতদাসী ছাড়া- অন্য সকলের থেকেই। আমি বললাম, হে রাসূল! লোকেরা যখন সফর ইত্যাদিকালে একত্রে উঠাবসা করবে তখন? বললেন : তখনও যতটা সম্ভব লজ্জাস্থান আবৃত রাখবে। আমি বললাম, আমাদের কেউ যখন একাকী থাকে, তখন? বললেন : আল্লাহ তা‘আলাকে অধিক লজ্জা করাই সকলের কর্তব্য। (আহম্মদ, আবু-দাউদ, ইবনে মাযাহ, তিরমিযী, হাকেম, বায়হাকী)
পরিচ্ছন্নতা ও সৌন্দর্য বিধায়ক দ্বীন
ইসলাম সৌন্দর্যর পূর্বে পরিচ্ছন্নতার ব্যবস্থা করার উপর অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। কেননা পরিচ্ছন্নতা সর্বপ্রকার সৌন্দর্য-শোভা ও চাকচিক্যের জন্যে ভিত্তিস্বরূপ কাজ করে রাসূলে করীম (সা) বলেছেন :
(আরবী*******************)
তোমরা সকলে পরিচ্ছন্নতা অবলম্বন কর। কেননা ইসলাম পরিচ্ছন্ন দ্বীন।
(আরবী*********************)
পরিচ্ছন্নতা ঈমান ডেকে আনে। আর ঈমান তার সঙ্গীকে নিয়ে জান্নাতে চলে যাবে। (তিবরানী)
নবী করীম (সা) শরীর, পোশাক, ঘর-বাড়ি ও রাস্তাঘাট পরিচ্ছন্ন করার ও রাখার জন্য উত্সাহ দিয়েছেন। বিশেষ করে দাঁত, হাত ও মস্তক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার জন্যে নির্দেশ দিয়েছেন।
পরিচ্ছন্নতার এ গুরুত্ব দ্বীন-ইসলামে কিছুমাত্র আশ্চর্যের ব্যাপার নয়। কেননা এ দ্বীনই নামাযের ন্যায় এক প্রাথমিক ইবাদতের জন্যে পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতাকে কুঞ্চিকার ন্যায় বলে ঘোষনা করেছে। এ কারণে নামাযীর নামায কবুল হয় না যদি না তার শরীর পোশাক ও স্থান পরিচ্ছন্ন থাকে। গোসল ও অযু দ্বারা যে পরিচ্ছন্নতা পবিত্রতা অর্জিত হয়, এ পরিচ্ছন্নতা তা থেকে ভিন্নতর জিনিস।
আরবীয় লোকেরা গ্রাম্য ও মরু পরিবেশে বসবাস করত। তার দরুন অনেক লোকই পরিচ্ছন্নতা ও সৌন্দর্যের ব্যাপারে তেমন সতর্কতা অবলম্বন করার প্রয়োজন মনে করত না। এ কারণে নবী করীম (সা) সব সময়ই তাদের মধ্যে পবিত্রতা-পরিচ্ছন্নতার অনুভূমি জাগিয়ে তুলতে চেষ্টা করতেন। তিনি প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের এতটা উন্নত করে তুলেছিলেন যে, তারা দুনিয়ার সেরা সভ্য জাতিতে পরিণত হয়েছিল। সব রকমের হীনতা, নীরবতা তাদের জীবনে অতীত হয়ে গিয়েছিল। ফলে তাদের অবস্থায় ভারসাম্যপূর্ণ সৌন্দর্য বিকশিত হয়ে উঠেছিল।
এক ব্যক্তি নবী করীম (সা) এর খেদমতে হাজির হয়েছিল। তার দাড়ি ও মাথার চুল অবিন্যস্ত অবস্থায় ছিল। রাসূল (সা) তার প্রতি এমন ভাবে ইঙ্গিত করলেন যে, মনে হলো, তিনি হয়ত তাকে চুল দাড়ি ঠিকঠাক করার নির্দেশ দিচ্ছেন। সে তাই করে চুল-দাড়ি ঠিকঠাক করে রাসূলের সম্মুখে হাজির হলো। তাকে দেখে নবী করীম (সা) বললেন : (আরবী**************)
এটা ভাল, না কারো এমন ভাবে আসা ভাল যে, তার মাথা আউলানো-ঝাউলানো থাকবে, যেন সে কতটা শয়তান।
নবী করীম (সা) অপর এক ব্যক্তিকে দেখলেন তার মাথার চুল আউলানো-ঝাউলানো। তিনি বললেন : (আরবী**********)
ও লোকটি মাথার চুলগুলো ঠিকঠাক করার জন্যে কি কিছুই পায়নি? ময়লা কাপড়-চোপড় পরা অপর একটি লোককে দেখে তিনি বললেন : ও লোকটি তা কাপড় পরিষ্কার করে ধৌত করার কি কিছুই পায়নি ? (আবু দাউদ)
রাসূলে করীম (সা) অপর একটি লোককে দেখতে পেলেন, যার পরণে খারাপ ধরনের কাপড় ছিল। তাকে বললেন :- তোমার কি ধন-মাল কিছু আছে ?
লোকটি বলল : জি হ্যাঁ। জিজ্ঞাস করলেন : কি ধরণের ধন-মাল? লোকটি বলল :
(আরবী******************)
আল্লাহ আমাকে সব ধরনের ধন-মাল দিয়েছেন।
তখন নবী করীম (সা) বললেন : (আরবী**********************)
আল্লাহ যখন তোমাকে ধন-মাল দিয়েছেন, তখন আল্লাহর নেয়ামত ও তাঁর অনুগ্রহের পরিচয় তোমার ওপর থেকে যাওয়া বাঞ্ছনীয়। (নিসায়ী)
নবী করীম (সা) জুম‘আ ও দুই ঈদ ধরনের জন-সম্মেলনসমূহের ক্ষেত্রে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নাতার সুষ্ঠু ব্যবস্থা রক্ষার জন্যে বিশেষ তাগিদ করেছেন। তিনি বলেছেন : (আরবী******************)
সম্ভব হলে কাম-কাজের কালে পরা দুখানি কাপড় ছাড়া জুমা‘আর দিনে ভিন্ন দুখানি কাপড় পরিধান করা কর্তব্য। (আবু দাউদ)
স্বর্ণ ও রেশমী কাপড় পুরুষদের জন্যে হারাম
ইসলাম যেখানে সৌন্দর্যকে বৈধ এবং কাম্য ঘোষণা করেছে এবং তাকে হারাম মনে করতে নিষেধ করেছে- যেমন বলা হয়েছে :
(আরবী*******************)
বল, আল্লাহ তার বান্দাদের জন্যে যে সৌন্দর্য ও পবিত্র রিযকসমূহের ব্যবস্থঅ করেছেন, তাকে কে হারাম করেছিল? (সূরা আরাফ :৩২)
যেখানে পুরুষদের জন্যে দুই ধরনের সৌন্দর্যের জিনিস হারাম করা হয়েছে, যদিও তা মাহিলাদের জন্যে সম্পূর্ণ হালাল করা হয়েছে : প্রথম, স্বর্ণালংকার ব্যবহার।
দ্বিতীয়, খাঁটি রেশমী বস্ত্র পরিধান।
হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন : (আরবী*******************)
নবী করীম (সা) রেশম ডান হাতে নিয়ে এবং স্বর্ণ বাম হাতে নিয়ে বললেন : এ দুটি জিনিস আমার উম্মতের পুরুষ লোকদের জন্যে হারাম। (আহমদ, আবু দাউদ, নিসারী)
হযরত উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমি নবী করীম (সা) কে বলতে শুনেছি : (আরবী**************)
তোমরা রেশমী কাপড় পরিধান করবে না। কেননা যে লোক দুনিয়ায় রেশমী কাপড় পরিধান করবে, সে পরকালে তা পরতে পারবে না। (বুখারী, মুসলিম)
রেশমী পোশাক সম্পর্কে তিনি বলেছেন : (আরবী*****************)
এটা সেই লোকদের পোশাক, পরকালে যাদের কোন কিছুই প্রাপ্য নেই।
নবী করীম (সা) এক ব্যক্তির হাতে একটি স্বর্ণের অঙ্গুরীয় দেখতে পেলেন। তখন তিনি-সেটিকে টেনে বের করে দূরে নিক্ষেপ করলেন এবং বললেন : (আরবী**********************)
তুমি কি নিজ হস্তে স্ফূলিঙ্গ ধরে রাখতে চাও?
পরে নবী করীম (সা) উঠে চলে যাওয়ার পর লোকটিকে বলা হয়, তোমার আঙ্গুরীয় তুলে নাও এবং সেটা কাজে লাগাও। তখন সে বলল : (আরবী*********************)
না, আল্লাহর কসম। রাসূলে করীম (সা) যা দূরে নিক্ষেপ করেছেন আমি তা তুলে নেব না। (মুসলিম)
এই স্বর্ণের অঙ্গুরীয়ের ন্যায় আধুনিকাকালে বিলাসী ধনশালী লোকদের দেখা যায় স্বর্ণের কলম, স্বর্ণের সিগারেট লাইটার, স্বর্নের সিগারেট কেস ও স্বর্নের সিগারেট হোল্ডার প্রভৃতি ব্যবহার করতে। এ সবই হারাম।
তাবে রৌপ্য নির্মিত অঙ্গুরীয় ব্যবহার করা পুরুষের জন্যেও হালাল এবং মুবাহ করেছেন নবী করীম (সা)। বুখারী শরীফে হযরত ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : (আরবী***********************)
নবী করীম (সা) একটি রৌপ্যের অঙ্গুরীয় নানিয়েছিলেন এবং সেটি তার হাতেই শোভা পাচ্ছিল। পরে তা হযরত আবু বকরের হতে শোভা পেতে থাকে। তাঁর পরে হযরত উমরের হাতে এবং তার পর হযরত উসমানের হাতে। শেষ পর্যন্ত তা আরীস নামক কূপে পড়ে যায়। (বুখারী)
এ ছাড়া লোহা ও অন্যান্য তৈরী আঙ্গুরীয় ব্যবহার করা হারাম নয়। কোন অকট্য দলিল দ্বারাই তার হারাম হওয়ার কথা জানা যায় না এবং বুখারী শরীফে বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে, নবী করীম (সা) এক ব্যক্তিকে মোহরানা সম্পর্কে বলেছেন : (আবরী****)
কোন কিছু তালাশ করে নিয়ে আস, একটি লোহার আঙ্গুরীয়ই হোক না কেন।
ইমাম বুখারী এ হাদীসের ভিত্তিতে লৌহ নির্মিত অঙ্গুরীয় ব্যবহার জায়েয বলে মত প্রকাশ করেছেন।
তবে প্রকৃত কোন কারণ থাকলে রেশমী কাপড় ব্যবহার করা জায়েয হতে পারে। নবী করীম (সা) হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা) ও হযরত জুবাইর ইবনুল আওয়াম (সা) হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা) হযরত জুবাইর ইবনুল আওয়াম (রা) কে তাঁদের খোস-পাঁচড়া ও চুলকানি ধরনের রোগের কারণে রেশমী কাপড় ব্যবহার করার অনুমতি দিয়েছিলেন।
রেশম ও স্বর্ণ ব্যবহার পুরুষদের জন্যে হারাম করার কারণ
রেশম ও স্বর্ণালংকার ব্যবহার পুরুষদের জন্যে হারাম করার মৌল উদ্দেশ্যে হচ্ছে, তাদের অতি উত্তম নৈতিক প্রশিক্ষণ দান। কেননা দ্বীন-ইসলাম জিহাদ ও শক্তি প্রদর্শনের দ্বীন। তাই তা সর্বপ্রকার নৈতিক দুর্বলতা উচ্ছঙ্খলতা ও পতন থেকে পৌরুষকে রক্ষা করা ইসলামের লক্ষ্য। আল্লাহ তা‘আলা পুরুষকে এক বিশেষ ধরনের অঙ্গ সৌষ্ঠব ও সংগঠন কাঠামো দান করেছেন এবং তা নারী থেকে ভিন্নতর। কাজেই পুরুষদের উচিত নয় সুন্দরী নারীদের সেঙ্গে প্রতিযোগিতায় পড়ে মূল্যবান অলংকারাদি ও খুব চাকচিক্যপূর্ন পোশাক-পরিচ্ছদ পরতে শুরু করা। এতদ্ব্যতীত সামষ্টিক ও সামগ্রিক কন্যাণও এর মুলে নিহিত রয়েছে।
ইসলাম বিলাসিত, আরাম-আয়েশ ও জাঁকজমকের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। পুরুষদের জন্যে স্বর্ণালংকার ও রেশমী পোশাক হারাম করা এ সংগ্রামেরই একটি অংশ বিশেষ। কেননা বিলাসিতা ও আরাম-আয়েশ কুরআনের দৃষ্টিতে জাতীয় ধ্বংস ও বিপর্যয়ের কারন হয়ে দেখা দিতে পারে। তা সামষ্টিক জুলুম ও শোষণের ফসলও। কেননা মুষ্টিমেয় সংখ্যক লোক বিপল সংখ্যক লোককে এবং দরিদ্রদের শোষণ করেই এ বিলাসিতার পাহাড় জমা করে ও সীমাহীন আরাম-আয়েশ উপভোগ করে। আর এ শ্রেনীর লোকেরাই চিরকাল যে কোন সামাজিক সংশোধন ও সামষ্টিক কল্যাণ প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে শক্তি প্রতিরোধক হয়ে দাড়িয়েছে। এ পর্যায়ে কুরআনের ঘোষণা হচ্ছে : (আরবী************************)
আমরা যখন কোন দেশ ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত করি, তখন সেখানে সচ্ছল অবস্থার বিলাসী ও আরাম-আয়েশে নিমজ্জিত ব্যক্তিদের নিয়োজিত করি, তারা সেখানে আল্লাহর নাফরমানী করতে শুরু করে। তখন আযাবের ফয়সালা সেখানকার লোকদের ওপর কার্যকর করে দিই, সেটিকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দিই। (সুরা বনী ইসরাইল : ১৬)
(আরবী***********************)
আমরা যখন কোন ভয় প্রদর্শনকারীকে কোন লোকালয়ের প্রতি প্রেরণ করি এবং সে তা করতে শুরু করে, তখন সেখানকার সুখী বিলাসী বড় লোকেরা বলতে শুরু করে, তোমাদের যে দায়িত্ব সহকারে পাঠান হয়েছে, তা অস্বীকার করছি। (সূরা আস-সাবাঃ ৩৪)
কুরআনের এ ভাবধারা ও দৃষ্টিকোণের সাথে সামঞ্জন্য রক্ষা করেই নবী করীম (সা) বিলাসিতা ও আরাম-আয়েশের দ্রব্য-সামগ্রীকে মুসলিম জীবনে হারাম করে দিয়েছেন। তাই দেখতে পাই, একদিকে পুরুষদের জন্যে যেমন স্বর্ণালংকার ও রেশমী কাপড় হারাম করে দিয়েছেন, অপরদিকে ঠিক তেমনি পুরুশ-নারী- উভয়ের প্রতিই হারাম করে দিয়েছেন যাবতীয় স্বর্ণ ও রৌপ্যের তৈজস পাত্রদি।
এ ছাড়া এ ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক কারণও নিহিত রয়েছে। কেননা স্বর্ণ নগদ সম্পদ হিসেবে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাপনায় সংরক্ষিত মূলধন রূপে গণ্য। কাজেই তা পুরুষদের পক্ষ অলংকার বা পাত্র হিসেবে ব্যবহৃত হওয়া কোনক্রমেই বাঞ্ছনীয় হতে পারে না।
মহিলাদের জন্যে তা হালাল কেন
মহিলাদের জন্যে স্বর্ণালংকার ও রেশমী পোশাক ব্যবহার হারাম না করে মহিলাদের বিশেষ দিক গুলোর প্রতি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। নারী প্রকৃতি স্বভাবতঃই সৌন্দর্যপ্রবণ। রূপ চর্চা, প্রসাধন ও অলংকারাদি ব্যবহারের একটা স্বাভাবিক দাবি রয়েছে নারী চরিত্রে। তবে এসবের সাহায্যে ভিন পুরুষদের আকৃষ্ট করা ও তাদের মধ্যে অবৈধ যৌন প্রবৃত্তি জাগিয়ে তোলার কোন অনুমতি বা সুযোগ ইসলামে নেই। হাদীসে বলা হয়েছেঃ (আরবী****************)
যে নারীই সুগন্ধি লাগিয়ে ভিন পুরুষদের সান্নিধ্যে যায়, তার সুঘ্রাণ তারা পেয়ে যায়, সে ব্যভিচারীনী এবং তার প্রতি দৃষ্টিই ব্যভিচারী দৃষ্টি হয়ে দাঁড়ায়। (নাসায়ী, ইবনে খারা, ইবনে হারয়াশ)
নারী সমাজকে সতর্ককরণ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেছেনঃ (আরবী*******************)
মহিলারা যেন তাদের পা এমন জোরে না ফেলে, যাতে করে তাদের লুকিয়ে রাখা সৌন্দর্য প্রকাশিত ও গোচরীভূত হয়ে যেতে পারে। (সূরা নূরঃ ৩১)
মুসলিম মহিলার পোশাক
ইসলাম মহিলাদের জন্যে এমন পোশাক পরিধান হারাম করে দিয়েছে, যার ভেতর দিয়ে দেহের কান্তি (সৌন্দর্য) বাইরে প্রকাশিত হয়ে পড়তে পারে। অনুরূপভাবে যে পোশাকের দরুন দেহের বিশেষ বিশেষ অংশ উলঙ্গ হয়ে থাকে এবং তা দেখে পুরুষেরা যৌন উত্তেজনা বোধ করতে পারে, তেমন পোশাক পরাও মহিলাদের জন্যে সম্পূর্ণ হারাম। বক্ষদ্বয়, কোমর, উরু বা পিঠ ও পেট উলঙ্গ রেখে পোশাক পরা কোন মুসলিম মহিলার জন্যে আদৌ জায়েয নয়।
হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (সা) ইরশাদ করেছেনঃ (আরবি****************)
দুই ধরনের লোক জাহান্নামী হবে। এক ধরনের লোক হচ্ছে, সেসব জালিম শাসক-প্রশাসক, যাদের সঙ্গে গরুর লেজের মত চাবুক সবসময় ঝুলতে থাকবে এবং যা দিয়ে তারা লোকদের ওপর আঘাত করতে থাকবে। আর দ্বিতীয় হচ্ছে সেসব মেয়েলোক, যারা কাপড় পরিধান করেও ন্যাংটা থাকে। তারা পুরুষদের নিজেদের দিকে আকৃষ্ট করতে চেষ্টা করবে আর নিজেরাও পুরুষদের প্রতি ঝুঁকে পড়বে। তাদের মাথা উষ্ট্রের ঝুঁকেপড়া চুটের মতো হবে। তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না, তার সুগন্ধিও তারা পাবে না। যদিও জান্নাতের সুঘ্রাণ বহু দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়বে। (মুসলিম)
কাপড় পরা সত্ত্বেও যেসব নারী উলঙ্গ থাকে এ কারণে যে, তাদের কাপড় দেহের সর্বাঙ্গ আবৃত করে না, তাদের কাপড় এতই পাতলা যে, তার ভেতর দিয়ে দেহের কান্তি (সৌন্দর্য) ফুটে বের হয়ে আসে। আর এজন্যেও যে, তারা কাপড় পরবেই দেহের যৌন উত্তেজক অংশসমূহ উন্মুক্ত রেখে। এ উভয় অবস্থায়ই কাপড় পরার মৌল উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে। বর্তমানের আধুনিকারা এ ধরনের পোশাক পরতেই অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে।
এই নারীদের মাথাকে উটের চুটের মতো বলা হয়েছে এ কারণে যে, তারা তাদের মাথার চুলের খোপা মাথার ওপর খুব উঁচু করে বাঁধে। মনে হচ্ছে, নবী করীম (সা) ভবিষ্যতের অদৃশ্যকে তখনই সুস্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলেন। কেননা মেয়েদের চুল বাঁধার এই প্রচলন আধুনিক কালের। সেকালে এ অবস্থা ছিল না। একালে চুল সুন্দর করার ও তাতে খোপা বেঁধে ‘ফ্যাশন্যাবল’ বানানর জন্যে বিশেষ বিশেষ শহরে আধুনিক স্টাইলের ‘সেলুন’ গড়ে উঠেছে। এসব সেলুনকে আরবী ভাষায় (আরবি*************) ‘কাওয়াফির’ বলা হয়। প্রায় সর্বত্রই এগুলোর পরিচালনার দায়িত্ব পুরুষই পালন করছে। তারা তাদের এ শ্রমের বিনিময়ে মোটা মোটা পারিশ্রমিক দাবি ও আদায় করে থাকে। শুধু তা-ই নয়, মেয়েরা আল্লাহর দেয়া স্বাভাবিক চুলকে অ-যথেষ্ট মনে করে কৃত্রিম চুল ক্রয় করে নিজেদের মাথার চুলের সাথে একত্রিত করে নেয়।
অবস্থা হচ্ছে, একদিকে এক শ্রেণীর পুরুষ হাস্য, নম্রতা-মসৃণতায়, রূপ ও সৌনর্যে-এবং দেখতে শুনতে নারীদেরছাড়িয়ে যেতে চেষ্টা শুরু করে দিয়েছে। আর অপরদিকে নারীরা আকর্ষণীয়া হয়ে পুরুষদের আকৃষ্ট করতে চেষ্টা চালাচ্ছে সর্বতভাবে।
উপরিউক্ত হাদীসে একটি বিশেষ কথার দিকে ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। রাজনৈতিক স্বৈরাচার বা রাষ্ট্রীয় স্বৈরতন্ত্র ও নৈতিক বিপর্যয় এ দুয়ের মাঝে একটি গভীর সম্পর্ক রয়েছে। বর্তমান সময়ের অবস্থা এ কথার বাস্তবতা অকাট্যভাবে প্রমাণ করে। স্বৈরাচারী রাজনীতিকরা চিরকাল জাতিকে যৌন লালসাপূর্ণ কাজ-কর্মে মগ্ন রাখে এবং লোকদের ব্যক্তিগত ঝামেলা-জটিলতায় জড়িত করে জাতীয় সমস্যাবলী থেকে তাদের দৃষ্টি ভিন্নদিকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চায়, যেন তাদের স্বৈরতন্ত্রের প্রতি কারো নজর না পড়ে।
নারী ও পুরুষের মাঝে সাদৃশ্য সৃষ্টি
নবী করীম (সা) ঘোষণা করেছেন, নারীর জন্যে পুরুষালী পোশাক পরিধান করা এবং পুরুষদের জন্যে নারীসুলভ পোশাক পরা সম্পূর্ণ হারাম। (আহমদ, আবূ দাঊদ, নাসায়ী, ইবনে মাজা, ইবনে হাবান)
উপরন্তু তিনি পুরুষের সাথে নারীর এবং নারীর সাথে পুরুষের সাদৃশ্যকারীদের ওপর অভিশাপ করেছেন। (বুখারী)
সাদৃশ্যকরণ পর্যায়ে কথাবার্তা, গতিবিধি, চলাফেরা, ওঠাবসা ও পোশাক পরা ইত্যাদি সব ক্ষেত্রেই গণ্য। স্বীয় প্রকৃতিকে অস্বীকার করা ও স্বভাবের দাবিসমূহের প্রহিপূরণ করতে প্রস্তুত না হওয়া- তার বিপরীত আচর-আচরণ অবলম্বন করাই হচ্ছে মানব জীবনে ও সমাজ ক্ষেত্রে বিপর্যয় সৃষ্টি হওয়ার মৌল কারণ। পুরুষ এক বিশেষ স্বভাব-প্রকৃতির অধিকারী। নারীদের স্বভাব ও প্রকৃতি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরনের। একজনের স্বভাব প্রকৃতির সাথে অপর জনের স্বভাব-প্রকৃতির আদৌ কোন মিল বা সাদৃশ্য নেই। কিন্তু পুরুষ যখন ‘নারী’ হবার চেষ্টা চালায় এবং নারীরা পুরুষালী চালচলন ও স্বভাব-প্রকৃতি ধারণ করতে চায়, তখন চরম নৈতিক ও সামাজিক বিপর্যয়ই হয় অনিবার্য পরিণতি।
যে পুরুষকে আল্লাহ্ তা’আলা পুরুষ বানিয়েছেন, কিন্তু সে নিজেকে নারী বানাতে ও নারীর সাথে সাদৃশ্য করতে চায় এবং যে নারীকে আল্লাহ্ তা’আলা নারী বানিয়েছেন, কিন্তু সে নিজেকে পুরুষালী বিশেষত্বে ভূষিত করতে চায়, এ উভয়ের ওপর রাসূলে করীম (সা) অভিসম্পাত করেছেন, দুনিয়া ও আখেরাত উভয় ক্ষেত্রেই তারা অভিশপ্ত। আল্লাহর ফেরেশতাগণও এ অভিসম্পাতে একাত্ম।
এ কারণেই নবী করীম (সা)পুরুষদের জন্যে হলুদ বর্ণের কাপড় নিষেধ করেছেন। হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেনঃ (আরবি****************)
রাসূলে করীম (সা) আমাকে স্বর্ণের অঙ্গুরীয়, রেশমী পোশাক ও হলুদ বর্ণের কাপড় ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। (মুসলিম)
হযরত ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেনঃ রাসূলে করীম আমার পরনে দুখানি হলুদ কাপড় দেখতে পেয়ে বললেনঃ (আরবি****************)
এ হচ্ছে কাফিরদের কাপড়। কাজেই তুমি তা পরবে না।
খ্যাতি ও অহংকারের পোশাক
পানীয়, খাদ্য ও পরিধেয় সব পবিত্র জিনিসই মুসলমানের জন্যে হালাল। তবে তাতে শর্ত হচ্ছে তা গ্রহণে যেন সীমালংঘন করা না হয়। এবং কোনরূপ অহংকার ও গৌরব প্রকাশ না পায়।
আরবী পরিভাষায় ‘ইসরাফ’ বলতে বোঝায় হালাল জিনিসের মাত্রাতিরিক্ত ও সীমালংঘনমূলক ব্যবহার। আর অহংকারী গৌরবী মনোভাবও মানসিক ব্যাপার। বাইরে তার প্রকাশ খুব কমই ঘটে। নিজেকে বড় কিছু মনে করে অহমিকায় পড়ে যাওয়াই হচ্ছে অহংকার। অন্যদের তুলনায় নিজেকে বড় বলে জাহির করাই হচ্ছে গৌরব। আল্লাহ্ তা’আলা কুরআন মজীদে ঘোষণা করেছেনঃ (আরবি****************)
আত্মগৌরবে মগ্ন ও অহংকারী কোন ব্যক্তিই আল্লাহ্ পছন্দ করেন না, ভালবাসেন না। (সূরা আল-হাদীদঃ ২৩)
নবী করীম (সা) বলেছেনঃ (আরবি****************)
যে লোক তার কাপড় অহংকার সহকারে টানবে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তার প্রাতি নজরও দেবেন না। (বুখারী, মুসলিম)
অহংকার ও গৌরবের ভাবধারা থেকে মুসলমানকে দূরে রাখার জন্যেই নবী করীম (সা) খ্যাতি ও প্রসিদ্ধর পোশাক পরতে নিষেধ করেছেন। যে ধরনের পোশাক পরলে জনসাধারণ থেকে স্বতন্ত্র কেউ- এটা প্রকাশ পায় ও পোশাকের দরুন তার বড়ত্ব জাহির হয়, তা-ই হচ্ছে খ্যাতি ও প্রসিদ্ধির পোশাক। রাসূলে করীম (সা) বলেছেনঃ (আরবি****************)
যে লোক খ্যাতি ও সমৃদ্ধির পোশাক পরিধান করবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাকে লাঞ্ছণা ও অবমাননার পোশাক পরিয়ে দেবেন। (আহমদ, আবূ দাঊদ, নিসায়ী, ইবনে মাযাহ)
এক ব্যক্তি হযরত উমর (রা)-এর কাছে জিজ্ঞেস করলঃ আমি কোন ধরনের পোশাক পরব? তখন তিনি বললেনঃ (আরবি****************)
তুমি সেই পোশাক পরবে, যার দরুন নির্জ্ঞান-নির্বোধ লোকেরা তোমাকে হালকা ও অগম্ভির মনে করবে না (অর্থাৎ হীন ও নীচ ধরনের পোশাক) এবং বুদ্ধিমান লোকেরা তাতে কোন দোষ বের করতে না পারে (অর্থাৎ ভারস্যাম্য নষ্ট হয়, এমন পোশাক পরবে না)। (তিবরানী)
মাত্রাতিরিক্ত সৌন্দর্যের জন্যে আল্লাহ্ সৃষ্টি বিকৃতকরণঃ
সৌন্দর্য বৃদ্ধির চেষ্টায় এমন সব কাজ করা, যার ফলে আল্লাহর সৃষ্টিই বিকৃত হয়ে যায়, ইসলাম আদৌ তা সমর্থন করে না। কুরআন এ কাজকে শয়তানের ‘অহী’ বা পরামর্শ বলে অভিহিত করেছে। কুরআনের ঘোষণা অনুযায়ী শয়তান তার কু-প্ররোচনা সম্পর্কে নিজেই বলেছেঃ (আরবি****************)
আমি আমার অনুসরণকারীদের আদেশ করব। ফলে তারা আল্লাহর সৃষ্টিকেই বিকৃত করে দেবে। (সূরা আন-নিসাঃ ১১৯)
দেহে চিত্র অংকন, দাঁত শানিতকরণ ও সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্যে অপারেশন করান
শরীরে বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে নানা চিত্র অংকন করান এবং দাঁত শানিত করান ইসলামে নিষিদ্ধ। হাদীসে উদ্ধৃত হয়েছেঃ (আরবি****************)
যে মেয়েলোক দেহে উল্কি (সুচিবিদ্ধ করে চিত্র অংকন) করে, যে তা করায়, যে দাঁত শানিত বানায় এবং যে তা বানাতে বলে, এ সব কয়টি শ্রেণীর লোকের ওপরই নবী করীম (সা) অভিসম্পাত করেছেন। (মুসলিম )
উল্কি বানানর জন্যে সাধারণত নীল রং ব্যবহার করা হয় এবং খুবই বিশ্রী ধরনের চিত্রাদি অংকন করান হয়। তার ফলে মুখাবরণ ও হাত কুশ্রী হয়ে যায়। আরব এবং বিশেষ করে মেয়েরা এ কাজে তো অনেক দূর এগিয়ে গেছে। তারা তাদের সমগ্র গাত্রে এ উল্কি আঁকিয়ে থাকে। কোন কোন ধর্মানুসারী লোক তো তাদের দেবদেবীর ছবি ও প্রতীকসমূহের চিত্র আঁকিয়ে থাকে। খিৃস্টানরা নিজেদের হাত ও বুকের ওপর ক্রুশ-এর চিত্র আঁকায়।
এসব খারাবী ছাড়াও একটা বড় খারাবী হচ্ছে, উল্কি বানানর সময় দেহে সূচ বিদ্ধ করা হয় বলে তাতে খুবই কষ্ট ও যন্ত্রণা অনুভূত হয়। এ কারণে এ কাজ করা ও করান উভয়ই ইসলামে নিষিদ্ধ ও অভিশপ্ত।
‘অশর’ দাঁতসমূহকে শানিত ও তীক্ষ্ণ সরু বানান ও যে বানাতে বলে এ উভয়ের ওপর রাসূলে করীম (সা) অভিশাপ বর্ষণ করেছেন। যে নারী অন্যের দ্বারা এ কাজ করায়, তার ওপরও অভিসম্পাত। কোন পুরুষ এ কাজ করলে সেও সে অভিশাপের মধ্যে পড়ে যাবে নিঃসন্দেহে।
দাঁত সম্পর্কে একথা যেমন সত্য তেমনি দাঁতসমূহের মধ্যে খোদাই করা ও গর্ত রচনা করাকেও হারাম ঘোষণা করেছেন রাসূলে করীম (সা)। হদীসে উদ্ধৃত হয়েছেঃ (আরবি****************)
দাঁতসমূহের মধ্যে ফারাক ও খোদাই করায় যেসব স্ত্রীলোক সৌন্দর্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে, তাদের ওপরও রাসূলে করীম (সা) অভিসম্পাত করেছেন। কেননা তারা আল্লাহর সৃষ্টির স্বাভাবিক অবস্থাকে বিকৃতি করে দেয়।
নারীদের মধ্যে অনেকেরই মুখের দাঁতে স্বাভাবিকভাবে ফাঁক থাকে, অনেকের আবার তা থাকে না। যাদের তা থাকে না, তারা কৃত্রিমভাবে তা করিয়ে নেয়। ফলে সে লোকদের ধোকা দেয়। সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্যেই এ কৃত্রিমতায় আশ্রয় লওয়া হয়। এর ফলে ইসলামের দৃষ্টিতে তার স্বভাব-প্রকৃতিতিও কৃত্রিমতা এসে যায়। ইসলাম তা আদৌ বরদাশত করতে রাজী নয়।
উপরে যে হাদীসসমূহ উদ্ধৃত হয়েছে, তা সহীহ্। এসব হাদীসের ভিত্তিতে আমরা সৌন্দর্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে অপরেশন (অস্ত্রোপাচার) করান সম্পর্কে শরীয়তের হুকুম জানতে পারি। এ কালের দেহ ও যৌন আস্বাদন পূজারী সভ্যতাই এসব অস্ত্রোপাচারের প্রচলন করেছে। একালের বস্তুবাদী পাশ্চাত্য সভ্যতার এ এক অন্যতম অবদান বলতে হবে। লোকেরা এ প্ররোচনায় পড়ে নিজেদের নাক কিংবা বক্ষ (স্তন) প্রভৃতির আকৃতি মনমতো ও লোভনীয় বানাবার উদ্দেশ্যে পুরুষ ও নারী হাজার হাজার টাকা ব্যয় করছে। প্রকৃতপক্ষে এ ধরনের কাজ আল্লাহর অভিশাপই টেনে আনে। এ কাজ যেমন কষ্টদায়ক, তেমনি আল্লাহর বানান আকৃতিকে শুধু-শুধুই পরিবর্তন করার শামিল। আর আসলেও অস্ত্রোপাচারে যে পরিবর্তনটুকু আনা যায়, তা অতিসামান্য, প্রকৃত কোন পরিবর্তন সাধন সম্ভবই নয়। বড়জোর দৈহিক পরিবর্তনই করান যেতে পারে, আত্মিক নয়।
তবে যদি কারো কোন ক্রটি থাকে, যা মূল দেহ কাঠামোর ওপর অতিরিক্ত এবং সেটির কারণে কষ্ট অুনভূত হয় কিংবা মানসিক কুণ্ঠায় জর্জরিত হতে থাকে, তাবে তার চিকিৎসা করানয় কোন দোষ নেই। তবে উদ্দেশ্য হতে হবে শুধু সে অসুবিধাটা দূর করান। কেননা তাতে সে কষ্ট পাচ্ছে, জীবন অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছে। এটা জায়েয এজন্যে যে, আল্লাহ দ্বীনে আমাদের জন্যে কোন কষ্টের কারণ রাখেন নি। (আরবী*****************)
হাদীস থেকেও এ মতের সমর্থন পাওয়া যায়। হাদীসে সৌন্দর্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্য অস্ত্রোপাচার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কাজেই এ উদ্দেশ্যে অস্ত্রোপাচার করা হলে নিশ্চিয়ই অভিশাপের উপযুক্ত হতে হবে। কিন্তু কোন কষ্ট দূর করা বা প্রয়োজন পূরণ করার উদ্দেশ্যে তা করান হলে তাতে কোনই দোষ হতে পারে না।
ভ্রূ সরুকরণ
মাত্রাতিরিক্ত রূপ ও সৌন্দর্য অর্জনের আর একট আধুনিক উপায় হচ্ছে, চুল বা পশম উপড়ান। আর তা সাধারণত, কপালের ভ্রূ চুল উপড়িয়ে ভ্রূকে যথাসম্ভব সরু করা। কিন্তু এ কাজটি ইসলামের দৃষ্টিতে হারাম। রাসূলে করীম (সা) এ কাজ যে করে, তার উপর অভিশাপ বর্ষণ করেছেন। হাদীসে উদ্ধৃত হয়েছে। (আরবী**********************)
যে স্ত্রীলোক চুল বা পশম উপড়ায় এবং যে অপরের দ্বারা একাজ করায় রাসূলে করীম (সা) উভয়ের ওপর অভিশাপ বর্ষন করেছেন। (আবূ দাউদ)
চুল বা পশম উপড়ানর ব্যাপারটি আরও কঠিন হারাম হয়ে দেখা দেয়, যখন তা চরিত্রহীনা মেয়েদের নিয়মিত অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। এবং তাদের একটি বিশেষত্ব হয়ে দাঁড়ায়। হানাফী মাযহাবের কোন কোন আলেম বলেছেনঃ মেয়েদের মুখবণ্ডলের চুল উপড়িয়ে পরিষ্কার করা, লাল রঙ লাগান, নকশা আঁকা ও নখে পালিশ লাগানো জায়েয। তবে তা স্বামীর অনুমতিক্রমে হতে হবে। কেননা এসব কাজ সৌন্দযের অলংকারের মধ্যে গণ্য। কিন্তু ইমাম নববী মুখবণ্ডরের চুল বা পশম উপড়ানর তীব্র বিরোধিতা করেছেন। তিনি এ কাজকে পূর্বোদ্ধৃত হাদীসের ভিত্তিতে হারাম বলেছেন। অবশ্য আবূ দাউদ তার সুনান’ গ্রন্থে লিখেছেন, যে নারী তার ভ্রূতে নকশা ও ছবি বানিয়ে সেটিকে সরু করে, হাদীসে তাকে نامصه বলা হয়েছে। এতে এতে করে ইমাম নববীর মতের প্রতিবাদ হয়ে গেছে। কেননা মুখবণ্ডলের চুল বা পশম দূর করা অভিশপ্ত কাজের মধ্যে গণ্য নয়।
তাবারনী’ গ্রন্থে বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে, আবু ইসহাকের স্ত্রী যুবতী ছিলেন। সৌন্দযের পিপাসু ছিলেন। তিনি হযরত আয়েশা (রা) এর কাছে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞাস করলেন: স্ত্রী কি তার স্বামীর জন্যে মুখমণ্ডলের পশম দূর করতে পারে? হযরত আয়েশা (রা) বললেনঃ ‘কষ্টের ব্যপারগুলো সাধ্যমত দূর কর। (আরবী*******************)
চুলে জোড়া লাগান
স্ত্রীলোকের পক্ষে নিজের মাথার চুলের সঙ্গে অপরের চুলের (পরচুলা) জোড়া লাগিয়ে সৌন্দর্য বৃদ্ধি করাও হারাম। তা আসল চুল হোক, কি নকল চুল।
ইমাম বুখারী হযরত আয়েশা, আসমা, ইবনে মাসউদ, ইবনে উমর ও আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে হাদীস উদ্ধৃত করেছেনঃ
(আরবী*********১৩১************)
চুলে যে জোড়া লাগায় এবং যে অন্যদের দ্বারা একাজ করায়- উভয় নারীর ওপর রাসূলে করীম (সা) অভিশাপ বর্ষণ করেছেন।
নারী সম্পর্কে যখন একথা, তখন পুরুষরা একাজ করলে তো নিশ্চয়ই এ অভিশাপে পড়ে যাবে, তা নিঃসন্দেহে বলা চলে। নবী করীম (সা) এ কাজকে تد ليس অর্থাৎ প্রতারণা বলে অভিহিত করেছেন। এমনকি যে নারীর মাথার চুল কোন রোগের কারণে ঝড়ে পড়ে যায়, তার পক্ষে অন্য কারো চুল নিজের মাথায় জাড়ান জায়েয নয়। বিবাহের কনে- যাকে স্বামীর কাছে পাঠান হচ্ছে-তার জন্যেও এ কাজ হারাম।
হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, আনসার বংশের একটি মেয়ে বিয়ে দেয়ার পর রোগে মাথার চুল পড়ে যায়। সে তার নিজের মাথায় অন্য চুল লাগাবার ইচ্ছা করে। এ বিষয়ে নবী করীম (সা) কে জিজ্ঞাস করা হলে তিনি বললেনঃ (আরবী*********)
যে চুল জোড়া লাগায় এবং যে অন্য কারো দ্বারা একাজ করায়- উভয় নারীর উপরই আল্লাহ তা’আলা অভিশাপ বর্ষণ করেছেন।
হযরত আসমা (রা) তাঁর একটি মেয়েলি-লোগের কারণে চুল পড়ে যাওয়ায় এ কাজ করার ইচ্ছা প্রকাশ করলে নবী করীম (সা) উপরিউক্ত উক্তিই করেন।
সায়ীদ ইবনুল মুসাইয়্যিব বলেনঃ হযরত মুয়াবিয়া মদীনায় এলেন- এটাই ছিল তাঁর শেষ আগমন। তখন তিনি আমাদের সামনে ভাষণ দিলেন। ভাষণ ব্যাপদেশে তিনি এক গোছা চুল বের করলেন বললেনঃ (আরবী******************)
ইয়াহূদী ছাড়া আর কেউ এ ফ্যাশন করে বলে আমি মনে করি না। নবী করীম (সা) এ কাজকে মিথ্যা-ধোঁকা বলে অভিহিত করেছেন অর্থাৎ চুলের সাথে অপরের চুল জড়ান।
অপর এক বর্ননা মতে হযরত মুয়াবিয়া মদীনাবাসীদের বলেনঃ (আরবী**********************)
তোমাদের আলিমগণ এখন কোথায়? রাসূলে করীম (সা) এ ধরনের কাজ করতে নিষেধ করেছেন তা আমি নিজে শুনতে পেয়েছি। তাঁকে এ-ও বলতে শুনেছি যে, বনী ইসরাঈলী মেয়েরা যখন এ ফ্যাশন শুরু করেছিল তখনই তাদের ধ্বংস শুরু হয়ে গিয়েছিল। (বুখারী)
নবী করীম (সা) এ কাজকে মিথ্যা-ধোঁকা বলে অভিহিত করেছেন। তাতে এ কাজ নিষিদ্ধ হওয়ার তাত্পর্য স্পষ্ট হয়ে উঠে। আসলে এ কাজ এক প্রকার ধোঁকা ও প্রতারণাই বটে এবং তা মিথ্যার সাহায্যে। এ ধরনের কাজের অনুমতি থাকলে ধোঁকা প্রতারনা করাও জায়েয হয়ে যেত অথচ ইসলামে তা ভয়নক গুনাহর কাজ। নবী করীম (সা) বলেছেন। (আরবী************)
যে আমাদের ধোঁকা দেবে, সে আমার উম্মতের মধ্যে গণ্য নয়।
ইমাম খাত্তাবী বলেছেনঃ এ কাজ নিষিদ্ধ এজন্য যে, এতে মানুষকে ধোঁকা দেয়া হয়, প্রতারিত করা হয়। উপরন্তু এ কাজ দ্বারা আল্লাহর আসল সৃষ্টি রূপ পরিবর্তন করে দেয়া হয় এবং সেটাই হচ্ছে বড় অপরাধ। হযরত ইবনে মাসউদ বর্ণিত উপরে উদ্ধৃত হাদীসে এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর হাদীসসমূহে চুলের সঙ্গে চুল জড়ান ও মেশান-তা স্বাভাবিক হোক, কি কৃত্রিম –মূলত ধোঁকা ও প্রতারণারই কাজ। তবে চুলের সাথে চুল ছাড়া অন্য কিছু-সূতা বস্ত্রখণ্ড ইত্যাদি জড়ান হলে তা নাজায়েয হবে না। এ পর্যায়ে হযরত সাইদ ইবনে জুবাইর (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেনঃ (আরবী************)
সূতা, রেশম কিংবা খোপা বানানর পশম জড়ালে তা দোষের হবে না।
ইমাম আহমদ ইবনে আম্বলও তা জায়েয বলেছেন।
খেজাব লাগন
মাথার চুল ও দাড়িতে খেজাব লাগানর এক প্রকারের সৌন্দর্য-চর্চার ব্যাপার। ইয়াহুদী ও খ্রীস্টান প্রভৃতি আহলি কিতাব লোকেরা খেজাব লাগিয়ে দাড়ি ও চুলের রং পরিবর্তন করার পক্ষপাতি নয়। কেননা তাদের ধারণা হচ্ছে, সোন্দর্য-চর্চা ও রূপ বৃদ্ধিকরণ দ্বীনদারী ও আল্লাহ পরস্তির পরিপন্থী। আর দ্বীনদারীর ক্ষেত্রে দুনিয়াত্যাগী, বৈরাগী, বৈঞ্চব প্রভৃতি সীমালংঘন ও অতিরিক্ত বাড়াবাড়িকারীদের এ-ই হচ্ছে নীতি। কিন্তু রাসূলে করীম (সা) এ লোকদের অনুসরণ করতে ও অনুরূপ আচার-আচরণ অবলম্বন করতে নিষেধ করেছেন, যেন মুসলমানরা অন্তরের ও বাইরের দিক দিয়ে নিজেদের স্বতন্ত্র সত্তা ও নীতি আদর্শের বৈশিষ্ট্য ও বিশেষত্ব অক্ষুণ্ন রাখতে সক্ষম হয়। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, হযরত নবী করীম (সা) এ লোকদের অনুসরণ করতে ও অনুরূপ আচর-আচারণ অবলম্বন করতে নিষেধ করেছেন, যেন মুসলমানরা অন্তরের ও বাইরের দিক দিয়ে নিজেদেরও স্বতন্ত্র সত্তা ও নীতি-আদর্শের বৈশিষ্ট্য ও বিশেষত্ব অক্ষুণ্ন আখতে সক্ষম হয়। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, হযরত নবী করীম (সা) বলেছেনঃ (আরবী************************)
ইয়াহুদী খ্রিস্টানরা খেজাব লাগান না। তোমরা তাদের বিরোধিতা কর।
এ আদর্শটি মুস্তাহাব ধরনের, সাহাবীগণ তাই মনে করেছেন। কেননা এ আদেশটি থাকা সত্ত্বেও সকল সাহাবী খেজাব লাগান নি। যেমন হযরত আবু বকর ও উমর (রা) লাগিয়েছেন, কিন্তু হযরত আলী ও উবাই ইবনে কায়াব (রা) লাগান নি। (আরবী*****)
কিন্তু খেজাব কি দিয়ে লাগান হবে? কালো কিংবা যে কোন রঙ লাগন যায় কি? না, কালো খেজাব লাগন পরিহার করতে হবে? এ প্রশ্নের জাবাব এই যে, যেসব লোক বার্ধক্য পৌছে গেছে, তাদের পক্ষে কালো খেজাব লাগান বাঞ্ছনীয় নয়। কেননা মক্কা বিজয়কালে হযরত আবূ বকর (রা) তখন তাঁর পিতা আবু কাহাফাকে রাসূলে করীমের কাছে উপস্থিত করালেন, তিনি দেখলেন, তার মাথার চুল একেবারে সাদা হয়ে গেছে। তখন তিনি বললেনঃ (আরবী*********************)
এ চুলের রঙ পরিবর্তন করে দাও। তবে কালো রং পরিহার কর। (মুসলিম)
কিন্তু যে লোকের অবস্থা বা বয়স আবু কাহাফার মত হয়নি, সে যদি কালো খেজাব ব্যবহার করে তাহলে উপরিউক্ত হাদীস অনুযায়ীই নাজায়েয হবে না। ইমাম জুহরী এ মতই প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেনঃ (আরবী*******************)
আমাদের মুখমণ্ডল যখন তরজাতা ছিল, নব্যতা ও তারুণ্যপূর্ণ ছিল, তখন আমরা কালো খেজার ব্যবহার করেছি। কিন্তু যখন আমাদের মুখমণ্ডল ও দাঁতে পরিবর্তন শুরু হয়ে গেল, তখন আমরা তা ত্যাগ করেছি। (ফাতহুল বারী)
কালো খেজাব ব্যবহার করা সাধারণভাবেই জায়েয বলে মত জানিয়েছেন সায়াদ ইবনে আবূ ওয়াককাস, উকবা ইবনে আমের, হাসান ও হুসাইন এবং জরীর প্রমুখ সাহাবী (রা)
কিন্তু অপর কতক আলিমের মতে কালো খেজাব লাগান জায়েয নয়। তবে তাঁদের মতেও জিহাদের সময় শত্রু পক্ষকে ভীত-সন্ত্রস্ত্র করার উদ্দেশ্যে তা লাগান যেতে পারে, যেন শত্রুপক্ষ মনে করে যে, সেনাবাহিনীর সব লোকই যুবক। তাতে তারা অনেকটা শংকিত বোধ করবে। (আরবী***********)
হযরত আবূ যর গিফারী (রা) বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছেঃ (আরবী*********************)
বার্ধক্যের শ্বেত-শুভবর্ণ পরিবর্তন করার উত্তম দ্রব্য হচ্ছে হেনা ও কাতাম।
কাতাম হচ্ছে একটা ইয়েমেনী ঘাস। তার রক্ত লালমুখী কালো। আর হেনা বর্ণ লাল। হযরত হাসান (রা) বর্ণনা করেছেনঃ হযরত আবূ বকর হেনা ও কাতাম ইভয় প্রকার খেজাবই ব্যবহার করেছেন আর হযরত উমর (রা) কেবলমাত্র খালেস হেনাই ব্যবহার করেছেন খেজাব হিসেবে।
দাড়ি বাড়ানো-লম্বাকরণ
আমদের আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে গণ্য একটি ব্যাপার হচ্ছে দাড়ি বৃদ্ধিকরণ। হযরত ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা) বলেছেনঃ (আরবী**********************)
তোমরা মুশরিকদের বিরোধিতা কর এবং দাড়ি বাড়াও, আর গোফঁ কাট। (বুখারী)
وفروا দাড়ি বাড়াও’ অর্থাৎ দাড়ি রেখে দাও, ছেড়ে দাও- আপনা থেকে বাড়তে দাও। হাদীসে এ আদেশের কারণও বলা হয়েছে। তা হচ্ছে মুশরিকদের বিরোধিতা। আর এ মুশরিক বলতে অগ্নিপূজারী মজুদীদের বোঝান হয়েছে। কেননা ওরা দাড়ি কেটে ফেলত। ওদের অকেনে আবার দাড়ি আবার দাড়ি মুণ্ডনও করত। আর রাসূলে করীম (সা) এদেরই বিরোধীতা করতে বলেছেন। তিনি মুসলমানদের এমনভাবে গড়ে তুলতে ও প্রশিক্ষন দিতে চেয়েছিলেন, যেন তাদের স্বাতন্ত্র্য অক্ষুন্ন থাকে। যেন তারা ঈমান-আকিদার দিক দিয়েও যেমন মুশরিকদের থেকে ভিন্নতর, তেমনি ব্যহ্যিক দিক দিয়েও যেন স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন হয়ে ওঠে। তবে দাড়ি মুণ্ডনের ব্যাপারটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। কেননা তাতে যেমন প্রকৃতির বিরোধীতা হয় তেমনি নারীদের সাথে সাদৃশ্য সৃষ্টি করা হয় অথচ দাড়ি হচ্ছে পুরুষের লক্ষণ পরিচায়ক। বাহ্যিকভাবে তাই পুরুষকে নারী থেকে স্বতন্ত্র করে দেয়।
তবে দাড়ি ছেড়ে দেয়া- বাড়ানর এই নির্দেশটির অর্থ এই নয় যে, দাড়ির কোন কিছু আদৌ কাটা যাবে না। কেননা দাড়ি অনেক সময় সীমাতিরিক্ত মাত্রায় বেড়ে যায় যে তা দেখতেও খারাপ লাগবে। তাতে সে ব্যক্তির পক্ষে বিশেষ কষ্ট ও অসুবিদার কারণ দেখা দিতে পারে। তাই তার দৈর্ঘ্য-প্রস্থ থেকে কাটা যেতে পারে। তিরমিজী শরীফে হাদীস উদ্ধৃত হয়েছেঃ (আরবী********)
নবী করীম (সা) তাঁর দাড়ির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ থেকে কাটতেন।
প্রাচীনকালের লোকদের অনেকেই তা করতেন। ইয়ায বলেছেনঃ (আারবী************************)
দাড়ি মুণ্ডন করা, তা কেটে ছেটে সমান সমান বানান মাকরূহ। কিন্তু যদি বড় হয়ে যায়, তাহলে তা দৈর্ঘ্য-প্রস্থ থেকে কেটে ফেলা ভালই। (আরবী****************)
আবু শামাহ বলেছেনঃ এ কালে এমন লোক দেখা যায়, যারা দাড়ি মুণ্ডন করে অথচ অগ্নিপূজারীদের সম্পর্কে একথা সর্বজনবিদিত যে, তারা দাড়ি কর্তন করত।
এ পর্যায়ে আমি বরতে চাই, বহু সংখ্যক মুসলমান ইসলামের দুশমন, ইয়াহুদী ও খ্রিস্টান প্রভৃতি সাম্রাজ্যবাদীদের অনুসরণ করতে গিয়ে দাড়ি মুণ্ডন করতে শুরু করেছে। আর তা করে তারা সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে ওদের কাছে পরাজয় স্বীকার করে নিচ্ছে। কেননা বিজিত লোকেরাই বিজয়ী জাতির সংস্কৃতির অনুকরণ ও অনুসরণ করে থাকে অথচ রাসূলে করীম (সা) যে কাফিরদের বিরোধীতা করতে বলেছে এবং তাদের সাথে সাদৃশ্য রক্ষা করতে নিষেধ করেছেন, তা তারা বেমালুম ভুলে বসেছে। হাদীসে বলা হয়েছেঃ (আরবী***********************)
যে ব্যক্তি যে জাতির সাথে সাদৃশ্য রক্ষা করবে, সে তাদের মধ্যেই গণ্য হবে। বহু ফিকহবিদ দাড়ি বাড়ান সংক্রান্ত রাসূলে করীম (সা) এর হাদীসের প্রেক্ষিতে দাড়ি মুণ্ডন করাকে সম্পূর্ণ হারাম বলেছেন। কেননা এ আদেশ পালন করা ওয়াজিব। এই বিশেষ আদেশ মুশরিকদের বিরোধিতাকরণের ওপর ভিত্তিশীল। আর তাদের বিরোধিতা করা মুসলমানদের জন্যে ওয়াজিব। আগের কালের কোন লোক এই ওয়াজিব তরক করেছেন বলে কোন প্রমাণ নেই।
কিন্তু এ কালের কিছু কিছু আলিম কালের প্রভাব প্রভাবিত হয়েও সাধারণ প্রচলন দেখে বলতে শুরু করেছেন যে, দাড়ি মুণ্ডনে কোন দোষ নেই। তাঁরা আরও বলতে শুরু করেছেন যে, দাড়ি লম্বা করে রাখা রাসূলে করীমে (সা) এর নিজস্ব অভ্যাসগত কাজ ছিল। তা শরীয়তের কোন ব্যাপার নয় এবং তা ইবাদত পর্যায়বুক্তও নয়। কিন্তু সত্য কথা হচ্ছে দাড়ি ছেড়ে দেয়া- লম্বা করা কেবলমাত্র রাসূলের নিজের কাজ দ্বারাই প্রমাণিত নয়। তার সাথে কারণ হিসেবে যুক্ত রয়েছে কাফিরদের বিরোধিতা। ইমাম ইবনে তাইমিয়া লিখেছেন, সর্বক্ষেত্রে কাফির মুশরিকদের বিরোধিতা শরীয়তের নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের মধ্যে গণ্য। বাহ্যিক সাদৃশ্য প্রীতি প্রণয় ভালবাসা বন্ধুত্বের ভাব জাগিয়ে তোলে অন্তরের মধ্যে। ঠিক যেমন অন্তরের ভালবাসা বাহ্যিক সাদৃশ্য সৃষ্টি করে। মানুষের অনুভূতি ও বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে এর সত্যতা প্রমাণিত। তিনি আরও লিখেছন, কাফির মুশরিকদের বিরোধিতার আদেশ এবং তাদের সাথে সাদৃশ্যকরণের নিষেধ কুরআন, হাদীস ও ইজমা থেকে অকাট্যভাবে প্রমাণিত। আর যে জিনিস বা কাজে কোন খারাবীর করণ নিহিত, তাই হারাম বলা যাবে। কাফিরদের বাহ্যিক কাজ-কর্মের সাথে সাদৃশ্য খারাপ চরিত্র ও কার্যকলাপের অনুসরণের কারণ। বরং সাদৃশ্যের এ কাজের ধারা আকীদা-বিশ্বাস বলয় পর্যন্ত প্রভাবিত করতে পারে বলে আশংকা করা যায়। এ প্রভাবটা ধরা যায় না, কেননা তাতে যে আসল দোষের উদ্রেক হয়, তা বাহ্যত চোখে পড়ে না। কিন্তু তা একবার বসে গেলেই তা দূর করা খুব কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। কাজেই যা-ই কোন খরাবীর নিমিত্ত হবে, তাই শরীয়তের দৃষ্টিতে হারাম হবে, এতে কোন সন্দেহ নেই। (আরবী*******************)
সর্বশেষ উল্লেখ্য, দাড়ি মুন্ডন সম্পর্কে তিনটি কথা। একটি কথা হচ্ছে দাড়ি মুণ্ডন করা হারাম। দ্বিতীয় কথা, দাড়ি মুণ্ডন মাকরূহ।
এই কথাটি ফতহুল বারী গ্রন্থে কাযী ইয়াযের নামে উদ্ধৃত হয়েছে। তাতে দ্বিতীয় কোন ব্যক্তির নাম উল্লেখ করা হয়নি। আর তৃতীয় কথা হচ্ছে, তা জায়েয।
এ কালের বেশ কিছু সংখ্যক আলিম এ মত পোষন করলে এর মধ্যে মাঝামঝি, সত্য নিকটবর্তী ও অধিক ইনসাফপূর্ণ কথা হচ্ছে, দাড়ি মণ্ডন মাকরূহ, হারাম নয়। কেননা রাসূলে করীমের যে কোন আদেশই নিরংকুশভাবে ওয়াজিব হয়ে যায় না, যদিও কাফির মুশরিকদের বিরোধিতা করার কারণ ভিত্তি হিসেবে উদ্ধৃত হয়েছে। তার অতি স্পষ্ট দৃষ্টান্ত হচ্ছে ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানদের বিরোধিতা করার জন্য খেজাব লাগিয়ে বার্ধক্যের শ্বেতবর্ণ পাল্টে দিতে আদেশ করেছেন। কিন্তু কোন কোন সাহাবী এ আদেশ পালন করতে গিয়ে তা করেন নি। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে, এ পর্যায়ের আদেশ মুস্তাহাব পর্যায়ের।
এ কথা সত্য যে, আগের কালের কোন মুসলমান দাড়ি মুণ্ডন করেছেন বলে জানা যায় না। তা এজন্যেও তো পারে যে, সেকালে লোকেরা দাড়ি মুণ্ডন প্রয়োজন মনে করতেন না; বরং তা রাখাই তাদের অভ্যাসে পরিণত হয়ে গিয়েছিল।
ঘর-বসবাসের স্থান
ঘর কিংবা বসবাস করার স্থান লোকদের জন্যে এক সুরক্ষিত আশ্রায়স্থল। এ ঘরেই তাদের পারিবারিক ও দাম্পত্য জীবন জাপিত হয়ে থাকে। মানুষ নিজের ঘরে নিজেকে সর্বপ্রকার সামাজিক বিধিবন্ধন থেকে মুক্ত মনে করতে থাকে। মানুষ নিজের ঘরেই আরাম ও বিশ্রাম লাভ করে মনে পায় পরম প্রশান্তি। এ কারণেই আল্লাহ তা’আলা বান্দাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহাবলীর উল্লেখ প্রসঙ্গে বলেছেনঃ (আরবী******************)
আল্লাহ তা’আলা তোমাদের জন্যে তোমাদের ঘরগুলোকে শান্তির আকর বানিয়েছেন। (সূরা নহলঃ৮০)
নবী করীম (সা) প্রশস্ত ঘর-বাড়ি পছন্দ করতেন। তিনি এ ধরনের ঘর-বাড়িকে বৈষয়িক সৌভাগ্যের নিমিত্ত মনে করতেন। তিনি বলেছেনঃ (আরবী************************)
চারিটি জিনিস কল্যাণের আকর। তা হচ্ছে, পবিত্র চরিত্রবতী স্ত্রী, প্রশস্ত ঘর, ভাল প্রতিবেশী এবং উত্তম যানবাহন।
নবী করীম (সা) প্রায়ই দো’আ করতেনঃ (আরবী*********************)
হে আল্লাহ! তুমি আমার গুনাহ মাপ কর, আমার ঘরে আমার জন্যে প্রশস্ততা দাও এবং আমার রিযিক আমাকে বরকত দাও।
জনৈক লোক বললেনঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি প্রায়ই এই দো’আ কেন করেন? জবাবে তিনি বললেনঃ
(আরবী****************)
এই দো’আয় কি কোন একটি জিনিসও বাদ পড়েছে?
নবী করীম (সা) ঘর-বাড়ি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। যেন এই পরিচ্ছন্নতা-পরিচ্ছন্নতাবাদী দ্বীন-ইসলামের একটা বাহ্যিক প্রকাশ ও বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়াতে পারে এবং যেন এরই ভিত্তিতে মুসলমান সেসব লোক থেকে স্বতন্ত্র মর্যাদায় অভিসিক্ত হতে পারে, যাদের ধর্মে ময়লা-অপরিচ্ছন্নতাই হচ্ছে আল্লাহর নৈকট্য লাভের একমাত্র মাধ্যম। রাসূলে করীম (সা) ইরশাদ করেছেনঃ (আরবী************************)
আল্লাহ তা’আলা পবিত্র, তিনি পবিত্রতা পছন্দ করেন। তিনি দয়াবান, অনুগ্রহসম্পন্ন, দয়া অনুগ্রহ তিনি পছন্দ করেন। তিনি দাতা, দান তিনি পছন্দ করেন। অতিএব তোমরা সকলে তোমাদের ঘরের আঙ্গিনা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখ এবং ইয়াহুদীদের সাথে সাদৃশ্য রাখবে না। (তিরমিযী)
বিলাসিতা ও পৌত্তলিকতার প্রকাশ
মুসলমানদের জন্যে তাদের ঘর-বাড়ি তেল-বার্নিশ, চাকচিক্য ও বৈধ ধরনের রূপ-সৌন্দর্য দিয়ে সুসজ্জিত করা কিছুমাত্র নিষিদ্ধ নয়।
স্বয়ং আল্লাহ তা’আলাই বলেছেনঃ (আরবী**********************)
আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্যে যেসব রূপ-সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছেন, তা কে হারাম করে দিতে পারে?
বস্তুত মুসলমান তার ঘর-বাড়ি, পোশাক-পরিচ্ছদ এবং তার সাথে সংশ্লিষ্ট যাবতীয় জিনিস খুব সুন্দর সুগঠিত, সুসজ্জিত ও চাকচিক্যময় করে রাখবে, তা কিছু মাত্র নিষিদ্ধ নয়। কোন দোষ নেই তাতে।
নবী করীম (সা) বলেছেনঃ (আরবি****************)
যে লোকের হৃদয়ে একবিন্দু অহংকার থাকবে, সে বেহেশতে যেতে পারবে না। তখন একজন বললঃ ইয়া রাসূল! আমেদের একজন পছন্দ করে যে, তার কাপড়-জুতা খুবই সুন্দর হোক, এটাও কি অহংকারের মধ্যে পড়ে? রাসূল বললেনঃ মোটেই না। কেননা আল্লাহ্ সুন্দর, তিনি সুন্দর ও সৌন্দর্যকে ভালবাসেন। (মুসলিম)
অপর এক বর্ণনায় বলা হয়েছেঃ (আরবি****************)
একজন সুন্দর সুশ্রী ব্যক্তি নবী করীম (সা)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে বলল? আমি সৌন্দর্য পছন্দ করি, আমাকে তার অনেক কিছুই দেয়া হয়েছে যেমন দেখছেন। এমনকি জুতার ফিতার ক্ষেত্রেও কেউ আমার ওপর শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে যাক, তাও আমি পছন্দ করি না। হে রাসূল, এটাও কি অহংকারের মধ্যে গণ্য হবে? তিনি বললেন, না বরং অহংকার হচ্ছে প্রকৃত সত্যকে প্রত্যাখ্যান করা এবং লোকদের হীন ও নগণ্য মনে করা। (আবূ দাঊদ)
অবশ্য ইসলামে জীবনের কোন দিকেই অতিশয় বাড়াবাড়ি ও সীমাতিরিক্ততা আদৌ পছন্দ নয়। মুসলমানের ঘর-বাড়ি বিলাসিতা ও জাঁকজমকের লীলাকেন্দ্র হোক, নবী করীম (সা) এটাও পছন্দ করেন নি। কুরআনে তা নিষেধ করা হয়েছে অথবা পৌত্তলিকতার প্রকাশ হওয়াও পছন্দনীয় নয়। কেননা আল্লাহ্ তওহীদী দ্বীন পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে পূর্ণ শক্তিতে লড়াই করেছে।
স্বর্ণ-রৌপ্যের পাত্র
ঠিক এ কারণেই মুসলমানদের ঘরে স্বর্ণ-রৌপ্যের পাত্র ও খাঁটি রেশমের শয্যা থাকাটাও হারাম করে দেয়া হয়েছে। এ নীতির বিরোধিতার জন্যে নবী করীম (সা) কঠোর ভাষায় কঠিন পরিণতির কথা শুনিয়েছেন। উম্মে সালমা (রা) বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (সা) ইরশাদ করেছেনঃ (আরবি****************)
যে লোক স্বর্ণ-রৌপ্যের পাত্রে পানাহার করবে, তার পেটে জাহান্নামের আগুন টগবগ করতে থাকবে। (মুসলিম)
(আরবি****************)
রাসূলে করীম (সা) স্বর্ণ-রৌপ্যের পাত্রে পানাহার করতে, রেশমী ও মখমলের কাপড় পরিধান করতে এবং তার ওপর আসন গ্রহণ করতে আমাদের নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেনঃ এগুলো কাফিরদের জন্যে দুনিয়ায় এবং আমাদের জন্যে আখিরাতে প্রাপ্য। (বুখারী)
আর যা ব্যবহার করা হারাম, তা তোহফা বা অর্ঘ-উপহার হিসেবে দেয়াও হারাম, সাজ-সজ্জা সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য তার ব্যবহারও হারাম।
স্বর্ণ-রৌপ্যের পাত্র ব্যবহার ও রেশমের শয্যা গ্রহণ পুরুষ ও নারী উভয়ের জন্যেই হারাম। ঘর-বাড়ি বিলাসদ্রব্য থেকে মুক্ত ও পবিত্রকরণই এগুলোকে হারাম করার একমাত্র উদ্দেশ্য। ইবনে কুদামা এ পর্যায়ে খুব সুন্দর লিখেছেনঃ
হাদীসে সাধারণভাবেই এ কথাগুলো এসেছে বলে নারী-পুরুষ উভয়ের জন্যেই তা সমানভাবে হারাম। কেননা এগুলোকে হারাম করার উদ্দেশ্য হচ্ছে অপচয়, বেহুদা খরচ-গৌরব-গর্ব ও দরিদ্রদের মনে আঘাত দান বন্ধ করা। আর তা নারী-পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রেই সমান। তবে স্ত্রীলোকদের জন্যে অলংকারাদির ব্যবহার জায়েয শুধু এজন্যে, যেন তারা তাদের স্বামীদের জন্যে সাজ-সজ্জা করতে পারে। কেউ প্রশ্ন করতে পারেন, হারাম করার এই যদি কারণ হয়ে থাকে তাহলে ইয়াকূত-হীরা জহরত- মহামূল্য পাথরের বর্তনাদি হারাম হল না কেন? তার জবাব হচ্ছে, গরীব লোকেরা এসব জিনিসের সাথে পরিচিত নয়। কাজেই ধনী লোকেরা যদি তা ব্যবহার করে তাহলে গরীব লোকদের মন কষ্ট পাওয়ার কোন কারণ হয় না। তাছাড়া এসব মহামূল্য পাথর পরিমাণে খুব কমই থাকে বলে তা দিয়ে পাত্র বানানর কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। এ কারণেতা হারাম করার কোন প্রয়োজনই অবিশষ্ট থাকে না। কিন্তু স্বর্ণ-রৌপ্যের ব্যাপারটি ভিন্নতর। (আরবি****************)
এসব কারণ ছাড়া অর্থনৈতিক কারণও নিহিত রয়েছে এসব জিপিহ্ন হারাম হওয়ার পেছনে। সেদিকে পূর্বেই ইঙ্গিত শরেছি। মূলতঃ স্বর্ণ ও রৌপ্য আন্তর্জাতিক দৃস্টষ্টতে নগদ মূলধন বলে গণ্য। আল্লাহ্ তা’আলা তাকে ধন-মালের মূল্যমানরূপে নির্দিষ্ট করেছেন। তাতে এক প্রকারের প্রকাশ শক্তি নিহিত রয়েছে। তা মূল্য সমূহের মধ্যে সঠিক ভারসাম্য সৃষ্টি করে ও রক্ষা করে, তা বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়েরও কাজ করে। আল্লাহ্ তা’আলা এভাবে তার ব্যবহারের পদ্ধতি বলে দিয়ে মানুষকে তাঁর নিয়ামত দানে ধন্য করেছেন। মানুষ যেন তাকে আবর্তনের মধ্যে রাখে, এটাই আল্লাহ্ চান। তকে নগদ সম্পদ হিসেবে ঘরে বন্ধ করে বা পাত্র সৌন্দর্য সামগী করে বেকার ফেলে রাখবে- তা আল্লাহ্ তা’আলা আদৌ পছন্দ করেন না।
ইমাম গাযযালী এ বিষয়ে খুব সুন্দরভাবে লিখেছেনঃ
যে লোক দিরহাম বা দীনার প্রভৃতি স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে স্বর্ণ-রৌপ্যের পাত্র নির্মাণ করবে (বা ক্রয় করে রাখাবে) সে আল্লাহর নিয়ামতের না-শোকরিয়া করে। ধন-সম্পদ মজুদ করে রাখার চাইতে বেশি অপরাধ সে করে। নগর প্রশাসককে কাপড় বোনা বা ঝাড়ু দেয়ার নগণ্য কাজ- যা সাধারণ মানুষ করতে পারে- লাগালে যেমন হয় এও ঠিক তেমনি। সেগুলোকে এভাবে ব্যবহার করার পরিবর্তে সঞ্চয় করে রাখা বরং ভাল। কেননা পাকা মাটি, লোহা, সীসা ও তামা প্রভৃতি প্রবহমান জিনিসকে সংরক্ষিত করার জন্যে স্বর্ণ-রৌপ্যের স্থলাভিষিক্ত। আর তৈজসপত্র প্রবহমান জিনিসগুলো সংরক্ষিত রাখার জন্যেই হয়ে থাকে। কিন্তু পাকা মাটি ও লোহা দ্বারা নগদ সম্পদ লাভের উদ্দেশ্য হাসিল করা যায় না। যে লোক এ তত্ত্বের সাথে পরিচিত নয়, তার কাছে আল্লাহ্ প্রদত্ত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মাধ্যমে এ কথা স্পষ্ট হওয়া উচিত এবং তাকে এ হাদীস শুনিয়ে দেয়া উচিত যেঃ (আরবি****************)
যে ব্যক্তি স্বর্ণ-রৌপ্যের পাত্রে পানাহার করে, সে নিজের পেটে জাহান্নামের আগুন ভর্তি করে। (ইহইয়াউ উলুম)
এভাবে হারামের বিধান দেয়ার ফলে মুসলমানদের ঘরের কাজকর্মে কোনরূপ সংকীর্ণতার উদ্ভুব হবে- এমনটা মনে করা ঠিক নয়। কেননা এর বাইরে পবিত্র ও হালাল জিনিসসমূহের ক্ষেত্র অনেক প্রশস্ত। কাঁচ-চিনামাটি, তামা এবং এ ধরনের বহু প্রকারের ধাতব পাত্র অনেক উত্তম ও ঝকঝকে। তুলা, সূতা ইত্যাদির বিছানা-বালিশ অনেক আরামদায়ক।
ইসলামে প্রতিকৃতি হারাম
মুসরমানদের ঘর-বাড়িতে জীবের প্রতিকৃতি (Statue) সংরক্ষণকে ইসলাম হারাম করে দিয়েছে। সম্মানিত ব্যক্তিদের ছবি বা প্রতিকৃতিও এর অন্তর্ভুক্ত। এসব জিনিস কারো ঘরে থাকলে সেখান থেকে আল্লাহর রহমতের ফেরেশতা পালিয়ে যায়। রাসূলে করীম (সা) ইরশাদ করেছেনঃ (আরবি****************)
যে ঘরে ছবি বা প্রতিকৃতি অবস্থিত, সেখানে আল্লাহর রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করেন না।
বিশেষজ্ঞগণ তার কারণ নির্দেশ করে বলেছেন, ঘরের প্রাচীরে যারা জীবের ছবি ঝুলিয়ে রাখে, তারা কাফিরদের মতোই কাজ করে। কেননা কাফিররাই সাধারণত নিজেদের বাড়ি-ঘরের প্রাচীরের সাথে ছবি ও প্রতিকৃতি ঝুলিয়ে রেখে থাকে এবং সেগুলোর প্রতি সম্মান ও ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে থাকে। ফেরেশতাগণ এ কাজ পছন্দ করেন না বলেই তাঁরা এসব ঘর ত্যাগ করে চলে যান এবং তথায় ফিরে আসেন না।
ইসলামে প্রতিকৃতি নির্মাণকেও হারাম করে দেয়া হয়েছে। অমুসলিমদের জন্যে বানান হলেও তা জায়েয হবে না। রাসূলে করীম (সা) ইরশাদ করেছেনঃ (আরবি****************)
যে সব লোক এ সব ছবি ও প্রতিকৃতি রচনা বা নির্মাণ করে, কিয়ামতের দিন তারাই অধিক আযাবে নিক্ষিপ্ত হবে।
অপর একটি বর্ণনায় বলা হয়েছেঃ (আরবি****************)
এরা সেই লোক, যারা আল্লাহর সৃষ্টি কার্যের সাথে সাদৃশ্য করতে চেষ্টা করছে।
নবী করীম (সা) সতর্ক করে দিয়ে বলেছেনঃ (আরবি****************)
যে লোক কোন জীবের ছবি আঁকবে বা প্রতিকৃতি নির্মাণ করবে, কিয়ামতের দিন তাতে রূপ ফঁকে দেয়ার জন্যে তাকে বাধ্য করা হবে। কিন্তু সে তা কখনই পারবে না। (বুখারী)
প্রকৃত রূহ দিয়ে সেটিকে জীবন্ত বানানর দায়িত্ব দেয়ার অর্থ এ অসম্ভব কাজ করতে চাওয়ার শাস্তি তাকে দেয়া হবে। কেননা এ কাজে সে কখনই সক্ষম হবে না।
ছবি ও প্রতিকৃতি হারাম করার কারণ
(ক) ছবি ও প্রতিকৃতি হারাম করার অনেকগুলো করণ রয়েছে। তন্মধ্যে প্রথম উল্লেখযোগ্য কারণ হচ্ছে, তওহীদী বিশ্বাসের সংরক্ষণ এবং পৌত্তলিকতার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ কার্যাবলি পরিহার। কেননা পৌত্তলিকরা নিজেদের হাতেই ছবি ও প্রতিকৃতি নির্মাণ করে এবং সিটিকেই পবিত্র মনে করে তার পূজা-উপাসনা করে, তারই সম্মুখে বিনয়াবনত হয়ে মাথা ঠেকায়, দাঁড়ায়।
তওহীদী আকীদার ব্যাপারে ইসলাম অনমনীয়, ক্ষমাহীন। আর সেরূপ পওয়াটাই স্বাভাবিক। কেননা যে সব জাতি তাদের আদর্শ পূর্বপুরুষ ও জাতীয় হিরো পর্যায়ের লোকদের স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ ছবি ও প্রতিকৃতি নির্মাণ করে, কিছুকাল অতিবাহিত হয়ার পর তারাই সেই ছবি-প্রতিকৃতিকে ‘মহান পবিত্র-শ্রদ্ধেয়’ মনে করতে শুরু করে। সেগুলোকেই উপাস্য দেবতা মনে করে সেগুলোর পূজা করতে আরম্ভ করে। অলক্ষ্যে সেগুলোকে ভয় করে, সেগুলোর সন্তুষ্টি অর্জন করতে চেষ্টা করে, আশা-আকাঙ্খার পরিপূরণ করতে সচেষ্ট হয়। বরকত হাসিল করার উদ্দেশ্যে সেগুলোর সম্মুখে হাজির হতে শুরু করে। উদ্দ, সুয়া, ইয়াগুম, ইয়াউক ও নসর প্রভৃতি প্রতিমূর্তির পশ্চাতে এই ইতিহাসই নিহিত রয়েছে।
এ ব্যাপারে ইসলামের সতর্কতা কোন বিস্ময়কর ব্যাপার নয়। কেননা ইসলাম তো সর্ব প্রকারের বিপর্যয় ও ভাঙ্গনের পথ রুদ্ধ করনতে বদ্ধপরিকর। যেসব ছিদ্রপথে প্রকাশ্য শিরক বা গোপনীয় শিরক মানুষের মন-মগজে প্রবেশ করতে ও স্থান দখল করে তাদের মুশরিক বানাতে পারে অথবা যেসব পথে সমাজে পৌত্তলিকতা ও ধর্মীয় ব্যাপারে বাড়াবাড়ির প্রচলন হতে পারে, তা সব চিরতরে রুদ্ধ করে দেয়াই ইসলামের লক্ষ্য। এ ব্যাপারে ইসলামের অনমনীয় নীতি ও ভূমিক এজন্যও যে, ইসলামী শরীয়ত কোন এক কালের, এক যুগের বা এক দেশ ও বংশের লোকদের জন্যে নয়- তা সর্বকালের সকল মানুষের জন্যে জীবন-বিধান। তারা দুনিয়ার যে-কোন অংশে বা দেশেই বসবাস করুক না কেন, কিয়ামত পর্যন্ত সমস্ত মানুষই তা যথাযথ পালন করতে পারে।
(খ) ছবি ও প্রতিকৃতি রচনা হারাম হওয়ার আর একটি কারণ হলো প্রতিকৃতি বা ছবি নির্মাতা এ ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে পড়ে যে, সে বুঝি একটা জিনিসকে অনস্তিত্ব থেকে বের করে এনে অস্তিত্বসম্পন্ন করে দিতে সক্ষম হয়েছে অথবা মাটি, পাথর বা কালি-কলম দ্বারা একটা জীবন্ত সত্তা বানিয়ে ফেলেছে। বাস্তব ঘটনাবলীই এ ধারণার সত্যতা প্রমাণ করে। উল্লেখ করা যেতে পারে, একজন লোক একটি প্রতিকৃতি নির্মাণ করল। তার পরে সে দীর্ঘদিন পর্যন্ত তার তলায় অবস্থান করতে থাকল। প্রতিকৃতিটি যখন পূর্ণাঙ্গ তৈরী হয়ে গেল, তখন সে তার সম্মুখে দাড়িয়ে তার নাক-নকশা ও তার সূক্ষ্ম কারুকার্যমণ্ডিত সৌন্দর্য দেখে আত্মশ্লাঘায় মেতে উঠল ও অহংকারে স্ফীত হয়ে প্রতিমূর্তিটিকে লক্ষ্য করে বলতে লাগলঃ ওরে কথা বল, কথা বল, (যেন ওটা একটা জীবন্ত সত্ত্বা)।
ঠিক এ কারণেই রাসূলে করীম (সা) বলেছেনঃ (আরবি****************)
যে সব লোক এ ধরনের প্রতিকৃতি-প্রতিমূর্তি নির্মাণ করে, কিয়ামতের দিন তাদের আযাব দেয়া হবে এবং বলা হবেঃ তোমরা যা কিছু সৃষ্টি করেছিলে, তা এখন জীবন্ত করে দাও। (বুখারী, মুসলিম)
হাদীসে বলা হয়েছে আল্লাহ তা’আলা বলেছেনঃ (আরবি****************)
যে আমার সৃষ্টির ন্যায় সৃষ্টি কর্ম করতে চায়, তার তুলনায় অধিক জালিম আর কে হতে পারে? ওরা যব বা গমের একটা দানা সৃষ্টি করে দিক না! (কেমন ক্ষমতা বুঝব)। (বুখারী, মুসলিম)
(গ) এ কর্মে যারা নিজেদের উদ্দেশ্য সাধন করতে চায়, তারা কোন স্থানে গিয়েই থেমে যায় না। তারা নারীদেহের নগ্ন ও অর্ধনগ্ন ছবি ও প্রতিকৃতি বানাতে শুরু করে। পৌত্তলিকতা বোতপরস্তির প্রতীক ক্রুশ মূর্তি প্রকৃতি নির্মাণেও তারা একবিন্দু দ্বিধা বা সংকোচ করে না অথচ এ ধরনের জিনিস বানান মুসলমানের পক্ষে আদৌ জায়েয নয়।
(ঘ) এতে সন্দেহ নেই যে, প্রতিকৃতি বিলাসী জীবনের পরিচায়ক। বিলাসী ও জাঁকজমককারী ধনী লোকদের একটা চিরকালের রীতি, তারা নিজেদের প্রাসাদপম ঘর-বাড়িগুলোকে প্রতিকৃতি ও ছবি দিয়ে সজ্জিত করে রাখে। নিজেদের কক্ষসমূহের প্রাচীর ঢেকে দেয় ছবির পর ছবি লাগিয়ে। নানা ধাতু দিয়ে প্রতিকৃতি বানিয়ে শিল্প-দক্ষতা ও শিল্পপ্রিয়তা প্রমাণ ও প্রদর্শন করে। দ্বীন-ইসলাম সর্বপ্রকার বিলাস-ব্যসন সামগ্রী ও তার প্রকাশ প্রমাণের প্রতীকসমূহের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। মুসলমানদের ঘরে প্রতিকৃতির সমাবেশ বা অস্তিত্ব বরদাশত করা ইসলামের পক্ষে কোনক্রমেই সম্ভব নয় এবং তা সম্পূর্ণ হারাম ঘোষিত হওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নয়।
মহাপুরুষদের স্মৃতিরক্ষার উপায়
কেউ প্রশ্ন করতে পারে, জাতীয় ইতিহাসে যেসব মহাপুরুষ চিরস্মরণীয় কীর্তি রেখে গেছেন তাঁদের অবদান সমূহের কথা সকলের মনে চির জাগরুক করে রাখার জন্যে তাদের বস্তুগত প্রতিকৃতি (Statue) দাঁড় করিয়ে তাদের অনুগ্রহের স্বীকৃতি দেবে না, অনাগত বংশধরদের সম্মুখে তাদের চিরভাস্বর করে রাখবে না? জাতির স্মরণশক্তি তো খুব তেজস্বী নয়, মানুষ তো ভুলে যায় সব কিছু। কালের স্রোত তাদের বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন করে দেয়। এরূপ অবস্থায় প্রতিকৃতি নির্মাণ করতে দোষ কি?
এর জবাব হচ্ছে, ইসলাম ব্যক্তিত্বের প্রতি মাত্রাতিরিক্ত শ্রদ্ধা বা ভক্তি প্রদর্শন পছন্দ করে না। সে ব্যক্তিত্ব যত বড়, যত উঁচু এবং মৃত বা জীবিত- যাই হোক না কেন। নবী করীম (সা) বলেছেনঃ
তোমরা আমার প্রশংসায় বাড়াবাড়ি ও সীমালংঘন করো না, যেমন করে খ্রিস্টানরা ঈসা ইবনে মরিয়মের সীমালংঘনমূলক প্রশংসা করেছে। তোমরা বরং আমাকে বলবেঃ আল্লাহর দাস, তাঁর রাসূল।
সাহাবিগণ নবী করীম (সা)-এর সম্মানার্থে দাঁড়াতে ইচ্ছা করেছিলেন। কিন্তু তিনি নিজেই তাঁদের নিষেধ করে দিলেন। বললেনঃ (আরবি****************)
অনারব লোকেরা যেমন পরস্পরের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থে দাড়িয়ে থাকে তোমরা সেরূপ দাঁড়িয়ে যেও না। (আবূ দাঊদ, ইবনে মাযাহ)
রাসূলে করীম (সা)-এর দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পর তাঁর উম্মতের লোকেরা যেন তাঁর প্রতি মর্যাদা ও সম্মান বা ভক্তি-শ্রদ্ধা দেখাতে গিয়ে সীমা ছাড়িয়ে না যায়। বলেছেনঃ (আরবি****************)
আমার কবরকে কেন্দ্র করে তোমরা উৎসব করতে শরু করে দিও না।
তিনি আল্লাহর কাছে অহরহ দো’আ করতেনঃ (আরবি****************)
হে আল্লাহ্! আমার কবরকে তুমি পূজ্যমূর্তি হতে দিও না।
কিছুলোক রাসূলে করীম (সা)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে বলতে শুরু করলঃ
হে আল্লাহর রাসূল! হে আমাদের সর্বোত্তম ব্যক্তিত্ব;
হে আমাদের সর্বোত্তম ব্যক্তিত্বের সুযোগ্য পুত্র;
হে আমাদের সরদার, হে আমাদের সরদার-তনয়;
এসব শুনে নবী করীম (সা) বললেনঃ (আরবি****************)
হে লোকেরা! তোমরা আজ পর্যন্ত আমাকে যেভাবে ডাকতে, সম্বোধন করতে, সেভাবে ডাক! শয়তান যেন তোমাদের ধোঁকায় ফেলতে না পারে। আমি তো মুহাম্মদ, আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল। আল্লাহ্ আমাকে যে স্থান ও মর্যাদা দিয়েছেন, তোমরা যেন তার চাইতে উঁচুতে আমাকে উঠিয়ে দিতে না চাও। (নিসায়ী)
ব্যক্তিদের প্রতিকৃতি নির্মাণ করে মূর্তির ন্যায় স্থাপন করে তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং সেজন্যে হাজার হাজার টাকা ব্যয় করা- সম্মান প্রদর্শনের এ রীতি ইসলামে আদৌ সমর্থিত নয়।
শ্রেষ্ঠত্বের মিথ্যা দাবিদাররা এবং বাতিল ও মনগড়া ইতিহাস সৃষ্টিকারীরা এসব ষড়যন্ত্রমূলক উপায়ে দুনিয়ার জাতিসমূহকে বিভ্রান্ত করছে আবহমানকাল ধরে। আর জাতির প্রকৃত খাদেম ও কল্যাণকারীদের তারা কখনই লোকদের সম্মুখে আসতে দেয়নি, দূরে লুকিয়ে রেখেছে। পরিচিত হওয়ার বা তাদের চিনবার কোন সুযোগই হতে দেয়নি।
ঈমানদার লোক যে চিরস্থায়িত্বের কামনা করে তা কেবলমাত্র আল্লাহর কাছে থেকেই পাওয়া যেতে পারে। তিনিই জানেন সব গোপন ও লুকান কথা। আর তিনি কখনই কিছু ভুলে যান না। তাঁর কোন ভুল-ত্রুটি হতেই পারে না। কত শত বিরাট বিরাট ব্যক্তিত্বের নাম তাঁর কাছে স্থায়ী রেজিষ্টারে লিখিত হয়ে আছে, যদিও মানুষ তাদের জানে না, চিনে না। কেননা আল্লাহ্ নেক, মুত্তাকী ও অপরিচিত অজ্ঞাতনামা লোকদেরই পছন্দ করেন, কোন মজলিসে নেক, মুত্তাকী ও অপরিচিত অজ্ঞাতনামা লোকদেরই পছন্দ করেন, কোন মজলিসে আসীন থাকলে তাক চেনা যাবে না, অনুপস্থিত হলে তাকে কেউ সন্ধানও করবে না।
যদি চিরস্থায়িত্বই কাম্য হয়ে থাকে, তাহলে এ ধরনের প্রতিকৃতি বা মূর্তি দাঁড় করে তা লাভ করা সম্ভব হবে না। তার একটিমাত্র উপায় রয়েছে এবং সে উপায়ই ইসলামে পছন্দনীয়, সমর্থিত আর তা হচ্ছে, সে ব্যক্তিত্ব সমূহের স্মরণ লোকদের মন-মগজে দৃঢ়মূল করে বসিয়ে দিতে হবে। লোকদের মুখে মুখে তাদের গুণগান ও প্রশংসা উচ্চারিত ও ধ্বনিত হবে। তারা যেসব ভাল ভাল কল্যাণকর কাজ করেছেন, অতুলনীয় কৃতিত্ব রেখে গেছেন, সেসব দেখে অনাগত বংশধরেরা তাঁদের প্রশংসা ও গুণগান অনন্তকাল ধরে করতে থাকবে, তাই তো স্বাভাবিক।
রাসূলে করীম (সা), খুলফায়ে রাশেদুন, ইসলামের ঐতিহাসিক নেতৃবৃন্দ ও ইমাম মুজতাহিদগণের স্মৃতি কোন ছবি বা পাখন নির্মিত প্রতিকৃতি দিয়ে অক্ষয় ও চিরস্মরণীয় করে রাখা হয়নি। পাথর খোদাই করে তাঁদের প্রতিমূর্তি নির্মাণ করা হয়নি, বরং এক বংশের লোক তাদের পূর্ববংশের লোকদের- সন্তান, পিতা-মাতা-চাচা-দাদার কাছ থেকে তাদের অক্ষয়-অতুলনীয় কীর্তির কথা মুখে মুখে- স্মৃতিশক্তি থেকে স্মৃতিশক্তিতে স্থানান্তরিত হতে হতে এ পর্যন্ত চলে এসেছে, মুখে মুখে তাদের কল্যাণময় উল্লেখ হয়েছে, সভা সম্মেলনে তার ব্যাখ্যা করা হয়েছে, আলোচনা হয়েছে। মানুষের মন ও মগজ তাদের কীর্তি গাঁথায় ভরপুর হয়ে রয়েছে এবং তা অনন্তকাল পর্যন্ত চলতে থাকবে অব্যাহতভাবে। কোনরূপ ছবি প্রতিকৃতি রচনা ছাড়াই তাঁর চিরস্মরণীয় ও অবিস্মরণীয় হয়ে আছেন এবং থাকবেনও চিরকাল।
[ দামেশক বিশ্ববিদ্যালয়ের শরীয়ত বিভাগের প্রাক্তন প্রধান আল-উস্তাদ মুহাম্মদ আল-মুবারক জামে আজহারে অনুষ্ঠিত এক সেমিনারে যে আলোচনা পেশ করেছিলেন, তার একটা অংশ এখানে উদ্ধৃত করছি। তিনি বলেছিলেনঃ বর্তমানে আমরা নতুন নতুন পরিবেশ পরিস্থিতি, সংগঠন ও সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানের সম্মুখীন হচ্ছি। কিন্তু তার মধ্যে অনেকগুলোই এমন যা আমাদের নির্ভুল আকীদা-বিশ্বাস ও চিরাচরিত নিয়ম-নীতির সাথে কিছুমাত্র সামঞ্জস্যশীল নয়। তার মধ্যে একটি হচ্ছে, জাতীয় ‘হিরো’ দের চিরস্মরণীয় করে রাখবার উদ্দেশ্যে ইউরোপ-আমেরিকায় অনুসৃত প্রতিমূর্তি নির্মাণ নীতি। আমরা যখন স্বাধীন ও প্রভাবমুক্ত দৃষ্টিতে চিন্তা করি, তখন দেখতে পাই যে, প্রাচীনকালের আরবরা তাদের বড় বড় লোকদের অপূর্ব ও ঐতিহাসিক কার্যকলাপ-যেমন জাতীয় স্বার্থে আত্মদান, তুলনাহীন দানশীলতা, বদান্যতা ও অপরিসীম সাহস-বীরত্বকে বিশেষ এক পন্থায় চিরস্মরণীয় করে রাখত। তাদের কিসসা-কিহিনীতে এবং সভা-সম্মেলনে এগুলোর ব্যাপক উল্লেখ হতো এবং বংশের পর বংশের লোকদের কাছে তা অবিস্মরণীয় করে রাখত। তাদের কাব্য-কবিতায় তাদের উচ্চ-প্রশংসা লিখিত হতো। ঐতিহাসিক হাতেম তায়ীর দানশীলতা ও উনশজার বীরত্ব কাহিনী এভাবেই চিরস্থায়ী হয়েছিল।
ইসলাম এসে এ পদ্ধতিকেই বলিষ্ট করে দেয়। আল্লাহর সেরা সৃষ্টি ও সর্বশেষ নবীকে একজন মানুষ হিসেবেই উপস্থাপিত করা হয়েছে। তাঁর নিজের মুখেই ঘোষণা করিয়েছেঃ (আরবি****************)
আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ। তবে আমার কাছে ওহী আসে।
এর ফলে মানুষের মূল্য ও মাপকাঠি হয়ে দাঁড়াল তাঁর আমল, তার দেহ নয়। রাসূলকে সকলেরই অনুসরণীয় আদর্শ ব্যক্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত করা হলো যেন সমস্ত মানুষ নিঃসংকোচে তাঁর অনুসরণ করতে পারে। সেই সঙ্গে ব্যক্তির পবিত্রতা ও শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন- তাকে এতটা বড় করে তোলা, যা ইবাদতে পর্যন্ত পৌঁছে যায়, পরিহার করা হলো। কেননা তাতে করে পরোক্ষভাবে মানুষকে হীন ও সামান্য-নগণ্য করা হয়।
এ কারণেই রাসূলে করীম (সা)-এর ইন্তেকাল হলে প্রথম খলীফা উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করলেনঃ (আরবি****************)
যে লোক মুহাম্মাদ (সা)-এর বন্দেগী করত, তার জানা উচিত যে, মুহাম্মাদ (সা) মরে গেছেন এবং যে লোক আল্লাহর ইবাদত করত, তার জানা উচিত, আল্লাহ চিরঞ্জীব, কখনই মরবেন না।
অতঃপর তিনি পাঠ করলেনঃ (আরবি****************)
মুহাম্মাদ (সা) রাসূল ছাড়া আর কিছুই নন। তাঁর পূর্বেও বহু রাসূল অতিবাহিত হয়ে গেছেন। এখন যদি সে মরে যায় বা নিহত হয়, তাহলে তোমরা কি পাশ্চাদপসরণ করবে?
ইসলাম মানুষকে চিরস্মরণীয় করে রাখে তার জনকল্যাণমূলক নেক আমলের মাধ্যমে এবং চিরস্থায়ী করে রেখেছে মুসলিম জনগণের মনে। তাঁদের বড় ছোট সকলেই সমানভাবে স্মরণীয় হয়ে আছেন তাঁদের নেক আমলসমূহের স্মৃতির মাধ্যমে। হযরত উমর (রা) সুবিচারপূর্ণ বলিষ্ঠ রাষ্ট্রনীতি ও রাষ্ট্র পরিচালন দক্ষতার দরুন, হযরত আবূ বকর দৃঢ় সংকল্প র নির্ভুল দূরদর্শিতার মাধ্যমে, হযরত আলী পরহেযগারী ও বীরত্বের মাধ্যমে অবিস্মরণীয় হয়ে আছেন লোকদের মনে-মগজে। তাদের চিরস্মরণীয় করে রাখার জন্যে পাথর নির্মিত প্রতিকৃতির ওপর নির্ভরশীল হতে হয়নি। তাঁদের কীর্তিই তাঁদের চিরস্মরণীয় করেছে, করেছে তাদের তুলনাহীন পবিত্র চরিত্র।
বস্তুতঃ প্রতিকৃতি নির্মাণ করে বড় লোকদের চিরস্মরণীয় করে রাখার নীতি গ্রহণ করা হলে পিছনের দিকে ফিরে যাওয়া হবে, প্রগতি হবে না হবে পশ্চাদগতি এবং উন্নত মর্যাদা থেকে হবে অধোগতি। রোমান গ্রীকরাই এ নীতি গ্রহণ করেছেন প্রথমে। পরে ইউরোপীয়রা তা অনুসরণ করেছে। কেননা এরা স্বভাবের দিক দিয়ে সকলেই পৌত্তলিকতাবাদী। ররা ব্যক্তিদের অপলনীয় কার্যবলীকে কার্যবলীকে র্যথার্থ মূল্য দেয়নি। বরং এজন্যে তাদের দেবতার মর্যাদা দিয়েছে। দেবতাদেরই বানিয়েছে জাতীয় হিরো।]
শিশুদের খেলনায় দেষ নেই
কিছু কিছু মূর্তি-প্রতিকৃতি এমনও হয়ে থাকে যেগুলো দ্বারা কারো প্রতি অসীম ভক্তি-শ্রদ্ধা দেখান হয় না, অতিশয় বিলাসিতা ও বড়লোকী দেখানও লক্ষ্য হয় না। তাছাড়া পূর্বোক্ত আলোচনায় যে আশংকা প্রকাশ করা হয়েছে, তারও কোন অবকাশ থাকে না। এ ধরনের মূর্তি-প্রতিকৃতি সম্পর্কে ইসলাম সংকীর্ণ মানসিকতা ও অসহনশীলতা প্রদর্শন করেনি। তাতে কোন দোষ্ণমনে করা হয়নি।
ছোট বালক-বালিকাদের খেলনা হিসেবে তৈরী মূর্তি-প্রতিকৃতিগুলো এ পর্যায়ে গণ্য। যেমন পুতুল, বিড়াল-কুকুর, পাখি প্রভৃতি জীব-জন্তুর মূর্তি। এগুলোর প্রতি কোনরূপ ভক্তিশ্রদ্ধা প্রকাশ করার বা অন্তরে থাকার কোন প্রশ্ন উঠে না। শিশুরা, বালক-বালিকারা তা নিয়ে শুধু খেলা করে, তার পূজা করে না। উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা) বলেনঃ (আরবি****************)
আমি রাসুলে করীম (সা)-এর উপস্থিতিতে মেয়েদের নিয়ে খেলা করতাম। আমার বান্ধবীরা আমার কাছে আসত ও রাসূলের ভয়ে লুকিয়ে যেত অথচ আমার কাছে ওদের আসা ও আমার সাথে খেলা করায় রাসূল খুশীই হতেন। (বুখারী, মুসলিম)
অপর একটি বর্ণনায় উদ্ধৃত হয়েছে, একদা নবী করীম (সা) তাঁকে বললেনঃ এগুলো কি? তিনি বললেনঃ এগুলো আমার পুতুল। বললেনঃ ওগুলোর মাঝখানে ওটা কি? বললেন? ওটা ঘোড়া। জিজ্ঞেস করলেনঃ ও ঘোড়াটির উপর কি? বললেনঃ ওদুটো পাখা। বললেন? ঘোড়ার আবার পাখা হয় নাকি?
হযরত আয়েশা (রা) বললেনঃ ‘আপনি কি শুনেন নি, দাঊদ-পুত্র হযরত সুলায়মানের পাখাওয়ালা ঘোড়া ছিল?’ এ কথা শুনে নবী করীম (সা) হেসে উঠলেন। সে হাসিতে তাঁর দাঁত মুবারক প্রকাশ হয়ে পড়ল। (আবূ দাঊদ)
হাদীসে যেসব পুতুলের উল্লেখ করা হয়েছে, তা নিয়ে বালক-বালিকারা খেলা করে। হযরত আয়েশা (রা) বিয়ের সময় খুবই অল্প বয়স্কা বালিকা ছিলেন।
ইমাম শাওকানী লিখেছেনঃ (আরবি****************)
উপরিউক্ত কথোপকথন সম্বলিত হাদীসটি প্রমাণ করে যে, বাচ্চাদের এ ধরনের প্রতিকৃতি দ্বারা খেলতে দেয়া জায়েয।
অবশ্য ইমাম মালিক (র) সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি এ ধরনের পুতুল ইত্যাদি খেলনা বাচ্চাদের জন্যে ক্রয় করে আনাকে মাকরূহ মনে করতেন। আর কাযী ইয়ায বলেছেন, ছোট ছোট মেয়েদের পুতুল দ্বারা খেলা করা জায়েয।
এ সব খেলনার মধ্যে সেসব পুতুলও শামিল, যা মিঠাই দ্বারা তৈরী করা হয় ও মেলা-তেহারে বিক্রয় হয়। বাচ্চারা তা নিয়ে কিছুক্ষণ খেলা করে। তারপর নিজেরাই তা খেয়ে ফেলে।
অসম্পূর্ণ ও বিকৃত প্রতিকৃতি
হাদীসে উদ্ধৃত হয়েছে, হযরত জিবরাঈল (আ) নবী করীম (সা)-এর ঘরে প্রবেশ করা থেকে একবার বিরত রয়েছিলেন এজন্যে যে, তাঁর ঘরের দ্বারপথে একটা প্রতিকৃতি রক্ষিত ছিল। দ্বিতীয় দিন এসেও প্রবেশ করেন নি। তখন তিনি নবী করীম (সা)-কে বললেনঃ (আরবি****************)
প্রতিকৃতিটির মস্তক ছেদন করে দিন। ফলে সেটি গাছের আকৃতি ধারণ করবে। (আর তা হলে তাঁর প্রবেশে কোন বাধা থাকবে না।) (আবূ দাঊদ, নাসায়ী, তিরমিযী)
একদল বিশেষজ্ঞ এই হাদীসের ভিত্তিতে বলেছেন যে, যে ছবি বা প্রতিকৃতি সম্পূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ, কেবল তা-ই হারাম। কিন্তু যে ছবি-প্রতিকৃতির কোন অঙ্গ নেই,- যে অঙ্গ ভিন্ন একটা জীবন্ত দেহ বেঁচে থাকতে পারে না, তা জায়েয।
আসল কথা হচ্ছে, হযরত জিবরাইল (আ) মস্তক ছেদন করতে বলেছিলেন যেন সেটার আকৃতি গাছের মত হয়ে যায়। এ থেকে বোঝা যায় যে, অঙ্গ ভিন্ন জীবন্ত দেহ বাঁচে না সেটার কথাই নয়। সেটাকে বিকৃত করাই হচ্ছে প্রকৃত কথা। যেমন সেটা এমন কোন আকার হয়ে না থাকে, যা দেখলে অন্তরে ভক্তি-শ্রদ্ধার ভাব জেগে উঠতে পারে।
একটু চিন্তা করলে ও ইনসাফের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিলে কোন সন্দেহ ছাড়াই আমরা বলতে পারি যে, ঘর সাজাবার উদ্দেশ্যে যেসব পূর্ণাঙ্গ প্রতিকৃতি স্থাপন করা হয়, রাজা-বাদশাহ-রাষ্ট্রনেতা-সৈনিক-কবি-সাহিত্যিকদের সেসব অর্ধাঙ্গ প্রতিকৃতির খুব বেশি করে হারাম হতে হবে, যা স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে মাঠে-ময়দানে চৌরাস্তায় সংস্থাপন করা হয়।
বিদেহী ছবি-প্রতিকৃতি
প্রতিকৃতি পর্যায়ে ইসলামের দৃষ্টিকোণ একক্ষণ আলোচিত হলো। এক্ষণে কাগজ, কাপড়, পর্দা, প্রাচীর, মেঝে, মঞ্চ ও মুদ্রা ইত্যাদির ওপর অংকিত শৈল্পিক ছবিসমূহ সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গী কি সেটাই প্রশ্ন।
তার জবাবে বলতে চাই, মূলতঃ ছবিটা কিসের, কোথায় রাখা হচ্ছে, কিভাবে তার ব্যবহার হবে এবং শিল্পী সেটা কি উদ্দেশ্যে বানিয়েছে, ছবি সম্পর্কে শরীয়তের ফয়সালা জানাবার পূর্বে এসব কথা স্পষ্ট হওয়া দরকার।
এসব শৈল্পিক ছবি যদি আল্লাহ্ ছাড়া যেসব মা’বুদ রয়েছে তাদের হয় যেমন ঈসা (আ)-এর ছবি, যাঁকে খ্রিস্টানরা নিজেদের মাবুদ বানিয়ে নিয়েছে কিংবা গাভী বা গরুর ছবি হয়, যা হিন্দুদের দেবতা- এ সবের ছবি যেহেতু এ উদ্দেশ্যেই নির্মাতা নির্মাণ করেছে, আর তারা কাফির। ছবির মাধ্যমে কুফরী ও গুমরাহী প্রচার করাই তাদের লক্ষ্য। এ সব ছবি অংকনকারীদের সম্পর্কেই নবী করীম (সা) কঠিন কঠোর বাণী শুনিয়েছেন। এ পর্যায়ে তাঁর বাণী হচ্ছেঃ (আরবি****************)
ছবি নির্মাতারাই কিয়ামতের দিন কঠিনতম আযাবে নিক্ষিপ্ত হবে। (মুসলিম)
তাবারী লিখেছেনঃ
এখানে সেই ছবি নির্মাতার কথা বলা হয়েছে যার বানান ছবির পূজা করা হয়। জেনে শুনে এ ধরনের ছবি বানান কুফরী কাজ। কিন্তু যে ব্যক্তি এ উদ্দেশ্যে নয়, অপর কোন উদ্দেশ্যে ছবি তোলে বা বানায়, সে শুধু গুনাহগার হবে।
যে লোক ছবিকে পবিত্র জ্ঞান করে প্রাচীরগাত্রে ঝুলায়, তার সম্পর্কে এই কথা। কোন মুসলিমই এ কাজ করতে পারে না। তবে যদি কেউ ইসলামই ত্যাগ করে, তবে তার কথা স্বতন্ত্র।
এরই অনুরূপ অবস্থা হচ্ছে এমন জিনিসের ছবি বানান, যার পূজা করা হয় না বটে, কিন্তু মূরত উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহর সৃষ্টিকর্মের সাথে সাদৃশ্য করা, অন্য কথায় ছবি নির্মাণ সে-ও যেন দাবি করছে যে, সেও আল্লাহরই মতো সৃষ্টি ও উদ্ভাবন ক্ষমতার অধিকারী।
এরূপ ব্যক্তি তার ইচ্ছা ও সংকল্পের কারণে দ্বীন-ইসলাম থেকে বহিষ্কৃত। এ ধরনের ছবি নির্মাতাদের সম্পর্কেই হাদীসে বলা হয়েছেঃ (আরবি****************)
কঠিনতম আযাবে নিক্ষিপ্ত হবে সেসব লোক, যারা সৃষ্টিকর্মে আল্লাহর সাথে সাদৃশ্য করে। (মুসলিম)
ব্যাপারটির সম্পর্ক ছবি-নির্মাতার নিয়তের সাথে। নিম্নোদ্ধৃত হাদীস থেকেও এ কথার সমর্থন পাওয়া যায়। তাতে আল্লাহর কথা উদ্ধৃত হয়েছেঃ (আরবি****************)
যে লোক আমার সৃষ্টির মতই সৃষ্টিকর্ম করতে শুরু করে, তার চাইতে বড় জালিম আর কেউ হতে পারে না। এ লোকেরা একটা দানা বা একটা বিন্দুই সৃষ্টি করে দেখাক না।
হাদীসটির শব্দসমূহ থেকে বোঝা যায়, সাদৃশ্য করার ইচ্ছা করা এবং ইলাহ হওয়ার বিশেষত্ব-সৃষ্টিকর্ম ও নবোদ্ভাবনে সমতা করা বুঝান হচ্ছে। আল্লাহ্ তা’আলা এ কাজকে চ্যালেঞ্জ করেছেন। বলেছেন, যদি বাস্তবিকই সাদৃশ্য করতে চাও, তাহলে একটা জীব বা দানা অথবা একটি বিন্দু সৃষ্টি করেই দেখাও না কেন? এ থেকে একথাও জানা যায় যে, সে লোক এ উদ্দেশ্য নিয়েই তা করেছিল। এ কারণে আল্লাহ্ তা’আলা কিয়ামতের দিন তাদের এ শাস্তি দেবেন যে, জনগণের সম্মুখেই তাদের নিজেদের সৃষ্ট দেহে প্রাণের সঞ্চার করার জন্যে বলবেন। কিন্তু তা করতে তারা কখনই সক্ষম হবে না।
ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ দিয়ে যেসব ছবি বা প্রতিকৃতিকে অত্যন্ত পবিত্র মনে করা হয় কিংবা বৈষয়িক দৃষ্টিতে তাদের সম্মানযোগ্য মনে করা হয় সেগুলো বানান এবং সংরক্ষণ হারাম। প্রথম প্রকারের ছবি ও প্রতিকৃতি হতে পারে নবী-রাসূল, ফেরেশতা ও নেককার লোকদের। যেমন হযরত ইবরাহীম, হযরত ইসহাক, হযরত মূসা, হযরত মরিয়ম ও হযরত জিবরাঈলের ছবি বা প্রতিকৃতি। খ্রিস্টানদের সমাজে এ পর্যয়ের ছবি ও প্রতিকৃতি সংরক্ষণের ব্যাপক রেওয়াজ রয়েছে। বহু বিদয়াতী মুসলমানও তাদের অনুসরণ করে। তারা হযরত আলী ও ফাতিমা (রা) প্রমুখের ছবি বা প্রতিকৃতি বানিয়ে থাকে।
আর দ্বিতীয় পর্যায়ের ছবি বা প্রতিকৃতি হয়ে থাকে রাজা-বাদশাহ, শাসক, ডিকটেটর ও শিল্পী-সাহিত্যিকদের। প্রথম প্রকারের ছবি প্রতিকৃতি বানানর তুলনায় এদেরটা বানান কিছুটা কম গুনাহ। কিন্তু বড় বড় কাফির, জালিম ও ফাসিক-ফাজির ব্যক্তিদের ছবি প্রতিকৃতি বানালে এ গুনাহ অধিক তীব্র হয়ে দেখা দেয়। যেমন সেসব শাসকদের ছবি প্রতিকৃতি, যারা আল্লাহর বিধান মুতাবিক শাসন কার্য সম্পন্ন করে না। সেসব নেতাদের বড় ছবি প্রতিকৃতি যারা আল্লাহর দেয়া জীবনাদর্শকে বাদ দিয়ে অন্য কোন দিকে লোকদের ডাকে। সেসব শিল্পী-সাহিত্যিকদের ছবি ও প্রতিকৃতি, যারা বাতিল মতাদর্শ প্রচার করে এবং লোকদের মধ্যে নির্লজ্জতা, নগ্নতা ও চরিত্রহীনতা প্রসার ঘটায়।
রাসূলের সমসাময়িক যুগে প্রধানতঃ পবিত্রতা ও সম্মান প্রদর্শনার্থেই ছবি বা প্রতিকৃতি বানান হতো। আর সেগুলোর বেশির ভাগ রোমান পারসিক অর্থাৎ খ্রিস্টান ও অগ্নি পূজারীদেরই কাজ হতো। এ কারণে সে সবের ওপরে ধর্মীয় ভক্তি-শ্রদ্ধা ও শাসকদের প্রতি পবিত্রতাবোধের ছাপ প্রকট হয়ে থাকত। হযরত আবুদ্ দোহা বলেনঃ (আরবি****************)
আমি মাশরূকের সাথে একটি ঘরে ছিলাম। তাতে বহু প্রতিকৃতি ও ছবি রক্ষিত ছিল। সেসব দেখে মাশরূক আমাকে বললেনঃ এগুলো কি কিসরা’র প্রতিকৃতি? আমি বললামঃ না, এ হযরত মরিয়মের প্রতিকৃতি। সম্ভবতঃ মাশরূক মনে করেছিলেন, এসব প্রতিকৃতি অগ্নি পূজারীদের নির্মিত! কেননা তারা পাত্রে ইত্যাদিতে নিজেদের রাজা-বাদশাহদের ছবি বানিয়ে থাকে। কিন্তু জানা গেল যে, এসব প্রতিকৃতি খ্রিস্টানদের নির্মিত। এ পর্যায়ে মাশরূক বললেনঃ আমি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলে করীম (সা) বলেছেনঃ আল্লাহর কাছে সর্বাধিক আযাব পাওয়ার যোগ্য সেসব লোক, যারা ছবি প্রতিকৃতি বানিয়ে থাকে।
এসব ব্যতীত উদ্ভিদ-গাছ, নদী, জাহাজ, পাহাড়, চন্দ্র, সূর্য, তারকা প্রভৃতি প্রাণহীন নৈসর্গিক দৃশ্যাবলীর ছবি বানান ও রাখায় কোন দোষ নেই। এ ব্যাপারে কোন দ্বিমতের অবকাশ নেই।
কিন্তু প্রাণীর ছবি হলে আর তাতে পূর্ববর্ণিত ভাবধারার আশংকা না থাকলে- শ্রদ্ধা – ভক্তি, সম্মান পবিত্রতার ভাবধারা জাগানর ছবি না হলে এবং তাতে আল্লাহর সৃষ্টিশক্তির সাথে সাদৃশ্যকরণ উদ্দেশ্য না হলে এ গ্রন্থকারের মতে তাতে কোন গুনাহ নেই, তা হারাম নয়। নিম্নোদ্ধৃত হাদীসদ্বয় থেকে তার সমর্থন পাওয়া যায়ঃ (আরবি****************)
আবূ তালহা সাহাবী থেকে বর্ণিত, রাসূলে করীম (সা) বলেছেন, ফেরেশতা এমন ঘরে প্রবেশ করে না, যেখানে ছবি রয়েছে। এই হাদীসের বর্ণনাকারী বুসর বলেছেন, পরে যায়েদ অসুস্থ হলে আমরা তাকে দেখতে গেলাম। দেখলাম, তার ঘরের দরজায় ঝুলান পর্দায় ছবি রয়েছে। রাসূলের বেগম মায়মুনার লালিত-পালিত উবায়দুল্লাহ খাওলানীকে জিজ্ঞেস করলাম, যায়েদ ছবি সম্পর্কে প্রথম দিন আমাদের কি বলেছিলেন? উবায়দুল্লাহ্ জবাবে বললেন, তিনি যে সময় ছবি হারম বলেছিলেন, তখন এই ব্যতিক্রমের কথাও বলেছিলেন যে, কাপড়ে অংকিত হলে দোষ নেই।
উতবা থেকে বর্ণিত, তিনি আবূ তালহা আনসারীকে দেখতে গেলেন। তথায় তিনি সহল ইবনে হানীফকে উপস্থিত পেলেন। আবূ তালহা এক ব্যক্তিকে বললেন, নিচ থেকে বিছানাটা বের করে আন। এ কথা শুনে সহল বললেন, ওটাকে কেন বের করে নিচ্ছ? তিনি বললেনঃ এজন্যে যে, ওটাতে ছবি রয়েছে। আর নবী করীম (সা) ছবি সম্পর্কে কি কি বলেছেন, তা তো আপনার জানাই আছে। সহল বললেন, তিনি এও বলেছেন যে, কাপড়ে অংকিত হলে দোষ নেই। আবূ তালহা ঠিকই বলেছেন, কিন্তু আমি মনে করি, ওটা সরিয়ে দেয়াই ভাল।
এ দুটো হাদীস থেকে কি প্রমাণিত হয় না যে, হারাম ছবি বলতে প্রতিকৃতি (Statue) বোঝায়। কিন্তু যেসব ছবি কাষ্ঠফলক, তক্তা বা শক্ত কাগজ বা কাপড়, বিছানা বা প্রাচীরের ওপর অংকিত করা হয়, সেগুলো যে হারাম, তা কোন সহীহ স্পষ্ট ও অকাট্য হাদীস থেকে প্রমাণিত নয়।
তবে সহীহ্ হাদীস থেকে একথা প্রমাণিত যে, নবী করীম (সা) এ ধরনের ছবির প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করেছেন। কেননা তাতে বিলাসিতা, বড়লোকী ও বৈষয়িক স্বার্থপূজার সাথে পূর্ণ সাদৃশ্য ও একত্মতা লক্ষ্য করা যায়।
হযরত আবূ তালহা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেনঃ আমি রাসূলে করীম (সা) কে বলতে শুনেছি, তিনি বললেনঃ (আরবি****************)
যে ঘরে কুকুর বা প্রতিকৃতি রয়েছে, তাতে ফেরেশতা প্রবেশ করে না।
তিনি বলেন, পরে আমি হযরত আয়েশা (রা)-এর কাছে জিজ্ঞেস করলাম। এই লোকটি বলেছেনঃ রাসূলে করীম (সা) নাকি বলেছেন যে, যে ঘরে কুকুর বা প্রতিকৃতি থাকবে, তাতে ফেরেশতা প্রবেশ করে না। আপনি কি শুনেছেন, রাসূল করীম (সা) এরূপ বলেছেনঃ তিনি বললেনঃ না। তবে আমি নিজে তাকে যা যা করতে দেখেছি, তা তোমার কাছে বর্ণনা করছি। রাসূলে করীম (সা) যুদ্ধে বের হয়ে গেলেন। তখন একটা চাদর দিয়ে দরজায় পর্দা করলাম। তিনি ফিরে এসে দরজায় সেই চাদরটি ঝুলতে দেখতে পেলেন। তাঁর চেহারায় অস্বস্তি ও অপছন্দের ভাব প্রকট হয়ে উঠল। পরে তিনি চাদরটি টেনে নিয়ে ছিড়ে ফেললেন এবং বললেনঃ আল্লাহ্ আমাদের পাথর ও মাটি সমূহ কাপড় দিয়ে সজ্জিত করার নির্দেশ দেন নি। হযরত আয়েশা (রা) বলেনঃ আমি সে কাপড় দিয়ে দুটি বালিশ বানালাম এবং তাতে খেজুর গাছের ছাল ভরে দিলাম। শেষে তিনি এ ব্যাপারে কোন আপত্তি করেন নি।
এই হাদীসটি থেকে খুব বেশি যা প্রমাণিত হয়, তা হচ্ছে এই যে, প্রাচীর ইত্যাদিকে ছবি যুক্ত কাপড় দ্বারা সাজ্জিত করা মাকরূহ তানজীহী মাত্র। ইমাম নববী লিখেছেনঃ (আরবি****************)
হাদীসটিতে এমন কোন কথা নেই, যা হারাম প্রমাণ করে। কেননা হাদীসের কথা ‘আল্লাহ্ আমাদের এর নির্দেশ দেন নি’ কথাটি দ্বারা না ওয়াজিব প্রমাণিত হয়, না হয় মুস্তাহাব। আর হারামও প্রমাণিত হয় না।
হযরত আয়েশা (রা) বর্ণিত অপর একটি হাদীস থেকেও এরূপ জানা যায়। হাদীসটি হচ্ছেঃ (আরবি****************)
আমার একটা পর্দার কাপড় ছিল। তার ওপর একটি পাখির ছবি অংকিত ছিল। কেউ ঘরে প্রবেশ করতে গেলে সেটার ওপর তার নজর পড়ত। এই দেখে নবী করীম (সা) আমাকে বললেনঃ ওটা সরিয়ে রাখ। কেননা আমি যখন ঘরে প্রবেশ করি, তখন ওটার ওপর আমার দৃষ্টি পরে ও দুনিয়া চোখের সম্মুখে ভেসে ওঠে।
নবী করীম (সা) পর্দার কাপড়টি ছিড়ে ফেলতে বলেন নি, সরিয়ে নিতে বলেছিলেন। এ কারণে যেসব জিনিস বৈষয়িকতা ও বৈষয়িক জাঁকজমক সুখ-স্বাচ্ছন্দের দৃশ্য স্মরণ করিয়ে দেয়, তার প্রতি আকর্ষন বৃদ্ধি করে নবী করীম (সা) সেসব জিনিস চোখের সুন্নাত ও নফল নামায সাধারণত নিজের ঘরেই পড়তেন। উপরিউক্ত ধরনের ছবি ও প্রতিকৃতি সম্বলিত চাদর ও পর্দা মানুষকে নিজেদের প্রতি নিরন্তর আকর্ষণ করতে থাকে। তার প্রভাবে আল্লাহর প্রতি ঐকান্তিক নতি স্বীকার ও একনিষ্টভাবে প্রার্থনা-মুনাজাতে নিমগ্ন হওয়া অনেকটা ব্যাহত হয়ে পড়ে। অন্তর গাফিল হয়ে যায়। হযরত আনাস (রা) বলেছেনঃ
হযরত আয়েশা (রা)-এর কাছে একটি পর্দার কাপড় ছিল। সেটা তিনি ঘরের একদিকে লাগিয়ে রাখতেন। নবী করীম (সা) তাঁকে বললেনঃ ওটাকে সরিয়ে রাখ। কেননা ওটার ওপর অংকিত ছবিগুলো নামাযে আমার সামনে পড়ে।
এ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, একটি পাখি ও অন্যান্য ছবি সম্বলিত কাপড়টির অস্তিত্ব নবী করীম (সা) বরদাশত করেছিলেন। কাপড় দুটি ছিড়ে ফেলার নির্দেশ দেন নি।
এ সব হাদীস ও এ ধরনের অপরাপর হাদীসের ভিত্তিতে সেকালের লোকদের মত হচ্ছে, যে ছবি বা প্রতিকৃতির ছায়া পড়ে- অন্য কথায় যা দেহসত্তা সম্পন্ন, কেবল সেগুলোই হারাম। পক্ষান্তরে যেগুলোর কোন ছায়া পড়ে না, তাতে কোন দোষ নেই।
ইমাম নববী মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যায় এই মতের প্রতিবাদ করে লিখেছেন, এ ধরনের মত বাতিল, গ্রহণ-অযোগ্য। কিন্তু হাফেজ ইবনে হাজার আল-আসকালানী ইমাম নববীর সমালোচনা করে বলেছেন, এই মতটি মদীনার সেকালের বিশিষ্ট ফিকাহবিদ কাসেম ইবনে মুহাম্মদ ঘোষণা করেছেন এবং সহীহ সনদ সহকারে বর্ণিত হয়েছে।
শায়খ বখীত ইমাম খাত্তাবীর উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। সে উক্তি এইঃ
যে ব্যক্তি জীব-জন্তুর আকৃতি বানায় আর যে শিল্পী বৃক্ষাদির ছবি আঁকে আমি মনে করি উপরিউক্ত কঠোর বাণী তাদের জন্যে নয়। যদিও এ পর্যায়ের সমস্ত কাজই অপছন্দনীয় এবং তাতে মানুষের লক্ষ্য অপ্রয়োজনীয় কাজকর্মের দিকে নিবদ্ধ হয়ে যায়।
খাত্তাবীর এই উক্তির উদ্ধৃতি দিয়ে শায়খ বখীত লিখেছেনঃ
তার কারণ হচ্ছে, যে ব্যক্তি জীবের আকৃতি রচনা করে, সে আসালে জীবের আ্কৃতি উদ্ভাবন করে না, আকার-আকৃতির একটা রূপ-রেখার তৈয়ার করে মাত্র। এভাবে যেসব ছবি আঁকা হয়, তাতে তার এমন বহু রূপ-প্রত্যঙ্গই উহ্য থেকে যায়, যা না হলে কোন জীবেরই জীবিত যাক সম্ভব হয় না। বরং আসলে দেহটাই অনুপস্থিত থাকে। কাজেই তা জীবের সেই ছবি নয়, যার অংকনকারী কিয়ামতের দিন রূহ ফুঁকে দেয়ার শাস্তির যোগ্য বিবেচিত হতে পারে অথচ সে তা করতে সক্ষম হবে না। যে ছবি আঁকা সম্পর্কে কঠোর বাণী উচ্চারিত হয়েছে, তা হচ্ছে দেহসম্পন্ন প্রতিকৃতি নির্মাণ, যার ছায়া হয়ে থাকে, যার কোন গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ যা না হলে জীবিত থাকতে পারে না- অনুপস্থিত থাকে না। যে প্রতিকৃতি এ ধরনের হবে, তাতেই রূহ ফুঁকে দেয়ার প্রশ্ন উঠতে পারে। কিন্তু ছবি অংকনকারী তাতে রূহ দিতে অক্ষম। তাহলে তার অর্থ এ নয় যে, প্রতিকৃতিটিএত জীবন গ্রহণের যোগ্যতাই নেই। বরং এটা ছকি অংকনকারীর অক্ষমতা। কাজেই তাতে অক্ষম হওয়ার দায়িত্ব তার ওপরই বর্তায়।
বিদেহী ছবি বানান যে জায়েয, নিম্নোদ্ধৃত হাদীস থেকেও তার সমর্থন পাওয়া যায়। আল্লাহর তা’আলা ইরশাদ করেছেন:
(আরবী******************)
তার তুলনায় অধিক জালিম আার কে হতে পারে, যে আমার সৃষ্টির ন্যায় সৃষ্টিকর্ম করে এদের তো উচিত একটা কণা সৃষ্টি করা, এদের তো উচিত একটা গমের দানা সৃষ্টি করা।
আসলে আল্লাহ তা’আলা সৃষ্টি- আমরা যেমন দেখছি- শুধু সমতল স্থানের ওপর রেখা মাত্র নয়, বরং তা দৈর্ঘ-প্রস্থসম্পন্ন দেহবিশিষ্বট সৃষ্টি। যেমন আল্লাহ নিজেই বলেছৈন:
(আরবী*****************)
সেই আল্লাহ্ই মাতৃগর্ভে যেমন চাহেন তেমন তোমাদের আকার-আকৃতি দিয়ে থাকেন।
এ মতের বিরুদ্ধে হযরত আয়েশা (রা) বর্ণিত হাদীসটিই দলিল হিসেবে পেশ করা যেতে পারে। হাদীসটি হচ্ছেঃ
(আরবী****************)
হযরত আয়েশা (রা) একটা বালিশ ক্রয় করেছিলেন। তার ওপর ছবি ছিল। রাসূলে করীম (সা) সেটা বাইরে থেকে দেখতে পেয়ে ঘরে প্রবেশ করলেন না, দরজাতেই দাঁড়িয়ে থাকলে হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমি রাসূলে করীমের চেহারা মুবারকে অস্বস্তি ও অসন্তুষ্টির চিহ্ন লক্ষ্য করে নিবেদন করলাম: হে রাসূলুল্লাহ! আমি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের দিকে প্রত্যাবর্তন করছি, আমার দ্বারা কি অপরাধ হয়ে গেল? বললেন: এ বালিশটি কোত্থেকে আলে? হযরত আয়েশা বললেন্: এ ধরনের ছবি যারা বানায়, কিয়ামতের দিন তাদের আযাব দেয়া হবে এবং তাদের বলা হবে, এখন তোমাদের সৃষ্টির মধ্যে প্রাণ দাও। পরে তিনি বললেন: যে খরে ছবি থাকে, ফেরেশতা সে ঘরে প্রবেশ করে না।
মুসলিম শরীফে উদ্ধৃত বর্ণনায় অতিরিক্ত কথা এটুকু:
(আরবী****************)
পরে আমি সেটা কেটে দুটি ছোট ছোট বালিশ বানালাম। রাসূলে করীম (সা) তার ওপর হেলান দেয়ার জন্যে ঘরে ব্যবহার করতে থাকলেন। হযরত আয়েশার কথার অর্থ হচ্ছে, ছবি সম্বলিত বালিশটিকে দুটি ছোট বালিশ বানিয়ে নিয়েছিলেন।
কিন্তু নিম্নোক্ত কয়েকটি ব্যাপার এ হাদীসের বিপরীত:
১. এক হাদীসটি বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত। বর্ণনাগুলো পরস্পরে বৈপরীত্য রয়েছে। কোন কোন বর্ণনা বলা হয়েছে, ছবি সম্বলিত বালিশটি কেটে দুটি ছোট বালিশ বানান হলো, যা তিনি ব্যবহার করতেন। কিন্তু অপর একটি বর্ণনায় বলা হয়েছে, তিনি তা ব্যবহার করেননি।
২. কোন কোন বর্ণনা থেকে তা ব্যবহ৮ার করা শুধু মাকরূহ মনে হয়। আর তাও ছবি সম্বলিত কাপড় দ্বার প্রাচীর সজ্জিত করা প্রসঙ্গে। তা এক প্রকারের বিলাসিতা ও বড়লোকি চাল। এ চাল রাসূলের আদৌ পছন্দ ছিল না। তিনি বলেছেন:
(আরবী*************)
পাথর ও মাটিকে পোশাক পরাবার কোন আদেশই আল্লাহ আমাদের দেননি।
৩. মুসলিম শরীফে স্বয়ং হযরত আয়েশা (রা) থেকেই ছবি সম্বলিত পর্দা সম্পর্কে যে হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে, তাতে নবী করীম (সা) নিজেই বলেছেন: ‘ওটা সরিয়ে রাখ, কেননা আমার নযর যখন ওর ওপর পড়ে তখন দুনিয়া আমার স্মরণে এসে যায়। এ কথা থেকে চূড়ান্ত ভাবে হারাম প্রমাণিত হয় না।
৪. সেই হাদীসটির বিপরীত, যাতে বলা হয়েছে, হযরত আয়েশা’র ঘরে যে পর্দা ছিল, রাসূলে করীম (সা) সেটাকে সরিয়ে নিতে বলেছিলেন। কেননা তাতে যে ছবি আঁকা রয়েছে, তা নামাযের সময়ে তাঁর সম্মেোখ এসে পড়ে। হাফেজ ইবনে হাজার বলেন: এ হাদীস ও হযরত আয়েশা’র বালিশ সম্পর্কিত হাদীস- এ দুটোর মধ্যে সমন্বয় সাধন কঠিন। কেননা এ হাদীস থেকে জানা যায়, পর্দাটি সরিয়ে ফেলার জন্যে নবী করীম (সা) আদেশ করেছিলেন এজন্যে যে, নামাযের সময় ছবিটি একেবারে চোখের সম্মুখে এসে পড়ে। নতুবা শুধু ছবির কারণে এ নির্দেশ তিনি দেন নি।
অতঃপর দুটি হাদীসের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের জন্যে তিন বলেছেন: প্রথম হাদীসে যেসব ছবির কথা রয়েছে তা প্রাণীর ছবি। আর এ হাদীসে যে ছবির উল্লেখ, তা প্রাণীর নয়।
কিন্তু এ সামঞ্জস্য বিধান যথার্থ নয়। কেননা পর্দা সম্পর্কি হাদীসে পাখির ছবির কথা উল্লেখ করা হয়েছে।
৫. আবূ তালহা বর্ণিত হাদীসও উপরিউক্ত হাদীসের বিপরীত। তাতে কাপড়ের ওপর অংকিত ছবিকে হারাম বলা হয়নি।
আল্লাম কুরতুবী লিখেছেন:
দুটো হাদীসের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের একটি উপায় হচ্ছে একথা বলা যে, হযরত আয়েশা বর্ণিত হাদীসে শুধু মাকরূহ বলা হয়েছে এবং আবূ তালহা বর্ণিত হাদীস থেকে শুধু জায়েজ প্রমাণিত হয়। আর তা মাকরূহ হওয়ার পরিপন্থী নয়।
হাফেজ ইবনে হাজারের মতে এ সমন্বয় উত্তম।
৬. হযরত আয়েশার ঠেসবালিশ সম্পর্কিত হাদীসের বর্ণনাকারী তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র কাসেম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর। তাঁর মতে যে ছবির ছায়া পড়ে না, তা জায়েয ছিল। ইবনে আউন বলেন: আমি কাসেমের কাছে গেলাম। তিনি মক্কার উচ্চাংশে নিজের ঘরে অবস্থান করছিলেন। আমি তাঁর ঘরে একটা সুসজ্জিত কোঠা দেখলাম। তার ওপর ‘কুন্দুস’ নামক এক প্রকারের জলজন্তু ও উমকা নামক এক প্রকারের পাখির ছবি অংকিত ছিল।
হাফেজ ইবনে হাজার বলেন:
সম্ভবতঃ যে হাদীসে (আরবী*********) তবে কাপড়ে অংকিত হলে (নাজায়েয নয়)’ কথাটি থেকে তিনি সাধারণভাবে জায়েয বুঝেছেন। আর সম্ভবনত হযরত আয়েশার ঘরের পর্দা সম্পর্কি হাদীসের ব্যাখ্যা তাঁর মতে এই ছিল যে, তার পর্দার কাপড়টি বিত্রিতও ছিল এবং তা প্রাচীল ঢাকার কাজেও ব্যবহার করা হতো। এ সম্পর্কেই রাসূলের কথা:” ‘মাটি ও পাথরকে কাপড় পরাবার আদেশ আমাদের দেয়া হয়নি।’ কাসেম ইবনে মুহাম্মদ মদীনার তদানীন্তন সাতজন বিশিষ্ট ফিকাহবিদের অন্যতম। তিনি হেলান দেয়ার বালিশ সম্পর্কিত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তিনি যদি ‘সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠ’ ধরনের ক্ষেত্রে ছবি থাকা জায়েয মনে না করতেন, তাহলে সেখানে তিনি নিশ্চয়ই তা ব্যবহার করতেন না। (ফাতহুল বারী)
কিন্তু ছবি ও ছবি অংকনকারী পর্যায়ে বর্ণিত এসব হাদীস থেকে একটি সম্ভবতক এই প্রকাশ পায় যে, রাসূলে করীম (সা) প্রথমদিকে- যখন শির্ক, বুতপরস্তি ও ও ছবিকে পবিত্র মনে করার কাল অতীত হয়েছে খুব বেশি দিন হয়নি- ছবির ব্যাপারে খুব কঠোর মনোভাব প্রকাশ করেছেন। কিন্তু উত্তরকালে তওহীদী আকীদা যখনে লোকদের মনে মগজে সুদৃঢ় হয়ে বসে গেছে, তখন বিদেহী ছবি রাখার অনুমতি দিয়েছেন- যা আসলে শুধু নকশা ও রেখামাত্র। তা-ই যদি না হবে, না হবে, তাহলে তাঁর নিজের ঘরে কোন ছবি সম্বলিত পর্দার অস্তিত্ত্বকেও তিনি আদৌ বরদাশ্ত করতেন না। আর কাপড়ে সৌন্দর্য বৃদ্ধি স্বরূপ অংকিত ছবিকে জায়েয বলতেন না। কাগজ ও প্রাচীরগাত্রে আঁকা ছবি সম্পর্কে এ থেকেই ধারণা করা যায়।
হানাফী মাযহাবের অন্যতম চিন্তাবিদ (ইমাম) তাহভী লিখেছেন: শরীয়তের বিধানদাতা শুরুতে সর্বপ্রকার ভচি-প্রকৃতিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। কাগজ বা কাপড়ে অংকিত চিত্র পর্যন্ত এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। কেননা মূর্তি-প্রতিকৃতি পূজার সময়কাল অতিবাহিত হয়েছে খুব বেশি দিন হয়নি। তখনো। এ কারণে সর্বপ্রকারের ছবি-চিত্রই নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। এ নিষেধ ঘোষণা কার্যকর হয়ে যাওয়ার পর তিনি কাপড়ে অংডিকত নক্শা-চিত্র ও নিষেধের আওতার বাইরে ঘোষণা করেন সাধারণ প্রয়োজনের দৃষ্টেোত। সেসব ছবিও জায়েয করে দেয়া হয়, যার প্রতি তেমন কোন সম্মান বা মর্যাদা দেখানো হয় না। যেসব ছবির অসম্মান করা হয় সেগুলোর প্রতি সম্মান বা মর্যদা দেখানোর আশংকা থাকে না। তবে সেসব ছবির প্রতি সাধারণতঃ অমর্যাদা দেখান হয় না, যে সবের ওপর নিষিধ পূর্ববৎ বহাল থেকে যায়। (আল জাওয়াবে শাফী)
ছবির প্রতি অমর্যাদাই তাকে জায়েয করে
কোন ছবিতে যদি এতটা পরিবর্তন সাধন করা হয়, যার দরযুন তা মর্যাদাযোগ্য থাকে না- অমর্যাদা সম্পন্ত হয়ে থাকে, তা বৈধতার আওতার মধ্যে এসে যায়। হাদীসে বলা হয়েছে, হযরত বিরাঈল (আ) ঘরে প্রবেশ করার অনুমতি চাইলে নবী করীম (স) বললেন:
(আরবী***************)
আসুন, জিরাঈল বললেন: আমি কি করে ঘরে প্রবেশ করব, আপনার ঘরে ছবি সম্বলিত পর্দা ঝুলছে! ওটা যদি রাখতেই হয়, তাহলে ছবির মাথা কেটে দিন কিংবা পর্দার কাপড়টি ছিড়ে বালিশ বা বিছানা বানিয়ে নিন।
এ কারণেইা হযরত আয়েশা (রা) যখন হেলান দেয়ার বালিশটির কারণে নবী করীম (স)-এর চেহারায় অস্বস্তির লক্ষণ দেখলেন, তখন ছিড়ে দুটো ছোট ছোট বালিশ বানিয়ে নিয়েছিলেন। এতে করে ছবির প্রতি গুরুত্বহীনতা প্রদর্শন করা হলো এবং কোনোরূপ সম্মান দেখানর আশংকা থাকে না।
আগের কালের লোকদের সম্পর্কে উদ্ধৃত হয়েছে যে, মর্যাদাহীন ছবি ব্যবহার করাতে তাঁরা কোন দোষ মনে করতেন না। ওরওয়া থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি পাখি ও মানুষের চিত্র সম্বলিত বালিশের ওপর হেলান দিতেন। ইকরামা বলেন, বলেন, ছবিকে প্রতিষ্ঠিত করা- উঁচু করে রাখাকে আলিমগণ পছন্দ করতেন না। আর যেসব ছবি সাধারণত পদদলিত হয়, তাতে তিনি দোষ মনে করতেন না। বালিশ-বিছানায় অংকিত ছবি তো পদদলিত হয়ই, এজন্যে তা জায়েয।
ফটোগ্রাফীর ছবি
এ কথা সুস্পষ্ট যে, প্রতিকৃতি নির্মাণ ও প্রতিকৃতি নির্মাতা পর্যায়ে যে সব হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে, তা সবই প্রতিকৃতি সম্পর্কে, যা খোদাই করা হয় কিংবা যা হাতে আঁকা হয়। কিন্তু ক্যামেরার দ্বার প্রতিবিম্বের সাহায্যে গৃহীত আলোক চিত্রের ব্যাপারটি সম্পূর্ণ নবোদ্ভাবিত। এ ফটোগ্রাফী রাসূলে করীমের যুগে ছিল না। এখানে প্রশ্ন ওঠে, প্রতিকৃতি ও প্রতিকৃতি নির্মাতা সম্পর্কে যেসব আইন-বিধান উদ্ধৃত হয়েছে, তা কি এই ফটোগ্রাফীর ওপর প্রযোজ্য?
সে সব আলিম মনে করেন, দেহ সম্পন্ন প্রতিকৃতি নির্মাণই হারাম, তাঁদের মতে ফটোগ্রাফীর ছবিতে কোন দোষ নেই, বিশেষ করে, যখন তা অসম্পূর্ণ অবস্থায় থাকে।
অপরাপর আলিমদের মত যা, সে পর্যায়ে প্রশ্ন হচ্ছে, এসব প্রতিবিম্ব সৃষ্ট ছবি কি সেই ছবির সমতুল্য, যা শিল্পী তার ব্রাশ দ্বারা নিজে আঁকে? কিংবা কোন কোন হাদীসে যেমন ‘ইল্লাত’ (Reason) হিসেবে বলা হয়েছে: প্রতিকৃতি নির্মাতা আল্লাহর সৃষ্টি কর্মের সাথে সাদৃশ্য করে, ফটোগ্রাফীতে কি তা উপস্থিত নেই? আর ফিকাহ্ দর্শনের দৃষ্টিতে ‘ইল্লাত’ (Reason)-ই যখন থাকে না, তখন তার ভিত্তিতে যে হুকুক-নির্তেষ করা হয়েছে তাও অবশিষ্ট থাকে না। (অর্থাৎ মূলত সাদৃশ্যই যখন নেই, তখন তা হারাম হতে পারে না।)
এ পর্যায়ে মিশরের মুফতি শায়খ মুহাম্মাদ বখীত মরহুম প্রদত্ত ফতোয়া অত্যন্ত সুস্পষ্ট। তিনি লিখেছেন: ফটোগ্রাফীর সাহায্যে গৃহীত ছবি- যা আলোর প্রতিবিম্বকে বিশেষ উপায়ে আটকে নেয়ার দরুন সম্ভবপর হয়- সেই ছবি প্রতিকৃতির অন্তর্ভুক্ত নয়, যা নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে। কেননা যে ধরনের ছবি-প্রতিকৃতি নির্মাণ করতে নিষেধ করা হয়েছে, তা হচ্ছে ছবি-প্রতিকৃতি উদ্ভাবন ও নির্মাণ করা প্রসঙ্গে, যা পূর্বে বর্তমান বা নির্মিত ছিল না, যা বানানর ফলে আল্লাহর সৃষ্ট কোন জীবন্ত জিনিসের সাথে সাদৃশ্য করা হয়। কিন্তু ক্যামেরার সাহায্যে গৃহীত ফটো সেই পর্যায়ে পড়ে না।
(আরবীঁ*****************)
বস্তুত ফটোর মূলকথা এবং শরীয়তের দৃষ্টিতে সে বিষয়ে হুকুম এই। তবে বহু আলিমই ছবি সম্পর্কে- তা যে ধরনেরই হোক না কেন- খুব কড়াকড়ি করে থাকেন এবং তা মাকরূহ (অনেকে স্পষ্ট হারাম) মনে করেন। ফটোগ্রাফীকে নাজায়েয মনে করেন। এতদসত্ত্বেও আলিমগণও প্রয়েঅজন ও জাতীয় বা তমদ্দুনিক কল্যাণে ছবি তোলা জায়েয বলেন, যেমন পরিচিত কার্ড বা পাসপোর্ট ইত্যাদির। বিশেষ করে সন্ধিগ্ন ব্যক্তিদের ছবি এবং ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ বা তওজীহর জন্যে ব্যবহৃত ছবি প্রভৃতি। এই ধরনের ছবি দ্বারা না কারো প্রতি কোনো শ্রদ্ধা-ভক্তি প্রদর্শন লক্ষ্য হয়, না এতে আকীদা খারাপ হওয়ার কোন আশংকা থাকতে পারে। কাপড়ে অংকিত চিত্রকে রাসূলে করীম (সা) হারামের মধ্যে গণ্য করেন নি। তাই তার তুলনায় অধিক বেশি প্রয়োজনীয় এ ধরনের ছবি তো অবশ্যই হারামের আওতা বহির্ভূত হবে।
ছবির উদ্দেশ্য
ছবি কি উদ্দেশ্যে বানান হচ্ছে, ছবির হারাম হওয়া না হওয়া এ প্রশ্নের খুব বেশি গুরুত্ব রয়েছে এবং এরই ভিত্তিতে তা নির্ধারণ করা সম্ভব, এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। যেসব ছবির উদ্দেশ্য ইসলামের আকীদা-বিশ্বাস, তার শরীয়ত এবং তার সংস্কৃতি ও রীতি-নীতির পরিপন্থী, তার হারাম হওয়ার ব্যাপারে কোন মুসলমানই দ্বিমত পোষণ করতে পারেন না। অতএব নারীদেহের নগ্ন বা অর্ধ নগ্ন ছবি এবং নারী বিশেষত্ব সম্পন্ত ও যৌন-উত্তেজনা বৃদ্ধি পেতে পারে যেসব অঙ্গ দর্শনে, সেসবের ছবি, সেসবের রেখাচিত্র বানাও সম্পূর্ণ হারাম। মানুষের মধ্যে যৌন-স্পৃহা ও তার উত্তেজনা বৃদ্ধি এবং হীন মন-মানসিকতাকে দাউ দাউ করা আগুনের মতো উত্তপ্ত করে দেয়ার লক্ষ্যে পত্র-পত্রিকাদিতে যে ধরনের ছবি বা স্কেচ প্রকাশ করা হয়, তা যে হারাম এবং তা যে অত্যন্ত মারাত্মক তাতে কোনই সন্দেহ থাকতে পারে না। এ ধরনের ছবি বা চিত্রের ব্যাপক প্রচার করা, ছাপানো ও সংরক্ষণ করা, ঘর অফিস ও প্রকাশ্য স্থানে ঝুলিয়ে রাখা, তার প্রদর্শনী করা, প্রাচীর গাত্রে তা লাগিয়ে রাখা- ইচ্ছা ও আগ্রহের বশবর্তী হয়ে তা দেখা ও পর্যবেক্ষণ করা সবই এ হারাম পর্যায়ের মধ্যে গণ্য।
কাফির-ফাসিক ও জালিম লোকদের ছবি সম্পর্কেও এ কথা। এ পর্যায়ের লোকদের ছবি প্রতিকৃতি রচনা বা সংরক্ষণ করা কোন মুসলমানের পক্ষেই শোভন নয়, উচিত নয়। যেসব নাস্তিক নেতা আল্লাহর অস্তিত্বকেই অস্বীকার করে, আল্লাহর শরীয়তকে অগ্রাহ্য করে কিংবা যেসব মূর্তিপূজারী আল্লাহর সাথে শিরক করার কাজে লিপ্ত, ইয়াহুদী ও খ্রিস্টন- যারা হযরত মুহাম্মাদ (সা)-এর নবুয়্যাতকে অস্বীকার করে কিংবা যেসব লোক মুসলিম হওয়ার দাবি করা সত্ত্বেও আল্লাহর নাযিল করা বিধানকে বাদ দিয়ে রাষ্ট্র শাসন, নীতি নির্ধারণ ও বিচার ফয়সালার কাজ করছে-স যারা সমাজের নির্লজ্জতা ও বিপর্যয় ছড়াচ্ছে- যেমন অভিনেতা-অভিনেত্রী, গায়ক-গায়িকা ও নর্তক-নর্তকী ইত্যাদিদের ছবিও সম্পূর্ণ হারাম।
যারা মূর্তিপূজার প্রসার ঘটায়, ইসলামের বিপরীত ধর্মের নিদর্শন- মূর্তি প্রতিকৃতি ও ক্রুশ ইত্যাদির ছবি কোনক্রমেই জায়েয নয়। রাসূলে করীম (স)-এর যুগে সম্ভবতঃ বেশির ভাগ বিছানার চাদর ও পর্দা-বালিশের কাপড়ে এ ধরনের ছবি চিত্রিত হতো। এ কারণে হাদীসে বলা হয়েছে:
(আরবী*************)
নবী করীম (সা) তাঁর ঘরে এমন কোন জিনিস রাখতেন না, যার ওপর ক্রুশ ইত্যাদির ছবি আছে। এরূপ জিনিস থাকলে তা ছিড়ে ছিন্নভিন্ন করে দিতেন।
হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে:
(আরবী***************)
মক্কা বিজয় বছরে যখন নবী করীম (সা) হারামের মধ্যে ছবি দেখতে পেলেন, তখন তিনি প্রবেশ করলেন না পরে তা মুছে ফেলা হয় এবং তার পরই তিনি তথায় প্রবেশ করেন।
সেখানে যেসব ছবি ছিলত তা থেকে মক্কার মুশরিকদের মূর্তিপূজা ও তাদের প্রাচীন গুমরাহীই প্রকট হয়ে উঠেছিল।
হযরত আলী (রা) বর্ণিত, নবী করীম (সা) একদা জানাযায় শরীক হয়েছিলেন। তখন বললেন:
(আরবী***********)
তোমাদের মধ্যে কে এমন আছে, যে মদীনায় গিয়ে প্রতিটি কবর সমতল করে দেবে এবং কোন একটি ছবিও রাখবে না, প্রত্যেকটিকেই বিকৃত করে দেবে?
এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললেন, ‘ইয়া রাসূল, আমি এ আঞ্জাম দেয়ার জন্যে প্রস্তুত। এ কথা শুনে মদীনাবাসীরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লো।.... পরে সেই লোকটি ফিরে এসে নিবেদন করলেন:
(আরবী****************)
হে রাসূল! আমি একটি মূর্তিও রাখি নি, চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছি। কোন একটি কবরকেও বাদ দেই নি, সবগুলোকে সমতল করে দিয়েছি এবং প্রতিটি ছবিকে আমি বিকৃত করে দিয়েছি, কোনটিকেই রেহাই দেইনি।
এ কথা শুনে নবী করীম (সা) ঘোষণা করলেন:
(আরবী*********)
অতঃপর যে লোকই এ কাজগুলোর মধ্যে থেকে কোন একটি কাজও করবে সে সেই হেদায়েতের অমান্যকারী হবে, যা মুমাহম্মাদ (সা) এর প্রতি নাযিল হয়েছে। (মুসনাদে আহমদ)
এ হাদীসে নবী করীম (স) যেসব ছবি বিকৃত করতে ও নির্মূল করতে নির্দেশ দিয়েছেন, সেগুলো জাহিলিয়াতের যুগের কুফরী ও শিরকের প্রতীক ও নিদর্শন ছাড়া আর কিছু নয়। এ কারণেই নবী করীম (স) এসব থেকে মদীনাকে মুক্ত ও পবিত্র করতে চেয়েছিলেন। আর এজন্যেই এসব কাজের মধ্যে কোন একটিও পুনরায় করাকে আল্লাহর নাযিল করা বিধানের প্রতি কুফরী ও অমান্য করার শামিল বলে ঘোষণা করেছন।
ছবি-প্রতিকৃতি ও তার নির্মাতা সম্পর্কিত বিধানের সার-নির্যাস
ছবি-প্রতিকৃতি ও তার নির্মাতা সম্পর্কে ইসলামী শরীয়তের যে বিধান বিস্তারিতভাবে আলোচিত হলো, তার সার-নির্যাস এইঃ
ক. আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য উপাস্য দেবতারূপে গৃহীতদের ছবি-প্রতিকৃতি সর্বাধিক কঠিন হারাম এবং তার গুনাহর সব চাইতে বেশি। খ্রিস্টানদের মাবুদ হযরত মসীহর (তাঁর মা মেরির) ছবি তার বড় দৃষ্টান্ত। এ ধরনের ছবি নির্মাণ সুস্পষ্ট কুফরী। কেউ যদি জেনে শুনে ইচ্ছা করে এ ধরনের ছবি নির্মান করে, তাহলে বুঝতে হবে, সে কাফির হয়ে গেছে। এ ধরনের ছবির প্রতিকৃতি নির্মান কঠিনতম গুনাহের কাজ ও অত্যন্ত জগণ্য ও ঘৃণ্য। আর যে ব্যক্তিই এ ধরনের ছবির প্রচলন করবে কিংবা কোন না কোনভাবে সে সবের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে, সে নিজের পরিমাণ অনুপাতে গুনাহে শরীক হলো।
খ. তার চাইতে কম গুনাহ হচ্ছে এমন সব ব্যক্তিত্বের প্রতিকৃতি নির্মান, যার পুজা করা না হলেও তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয়। যেমন কোন দেশের রাজা-বাদশা, সর্বোচ্চ নেতা, প্রশাসক, ডিকটেটর ইত্যাদি-এদের স্মৃতিস্তম্ভ স্বরূপ প্রতিকৃতি নির্মান করে উন্মুক্ত স্থানে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। প্রতিকৃতি অসম্পূর্ণ বা সম্পুর্ণ হওয়ার দিক দিয়ে গুনাহে কোন তারতম্য হয় না।
ঘ. এর চেয়েও কম গুনাহ হচ্ছে এমন সব ব্যক্তির প্রতিকৃতি নির্মাণ, যাদের তাযীম ও পবিত্রতা প্রদর্শন করা হয় না। তবে তাও হারাম, এ সম্পর্কে কোন দ্বিমত নেই। তবে যাদের প্রতি তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য জ্ঞাপন করা হয়, তা এ পর্যায়ে পড়ে না। যেমন বাচ্চাদের খেলনা ও মিঠাই মণ্ডা দিয়ে কোন প্রতিকৃতি বানান- যা খেয়ে ফেলা হয়।
ঙ. এর পরে আসে বিদেহী ছবিগুলোর প্রশ্ন। অর্থাৎ শৈল্পিক ছবি সেসব ব্যক্তিত্বের যাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয়, যেমন প্রশাসক, জননেতা, রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাতা প্রমুখের ছবি। বিশেষ করে যদি তা কোথাও স্থাপন করা বা ঝুলিয়ে দেয়া হয়। হারামের মাত্রা আরও কঠিন ও তীব্র হয়ে ওঠে যদি জালিম, ফাসিক-ফাজির-নাস্তিক ইত্যাদি ধরনের লোকদের ছবি হয়। কেননা এসব লোকের প্রতি তাযীম-সম্মান-উক্তি দেখান ইসলামকে নির্মূল করার সমান অপরাধ।
চ. গুনাহর দৃষ্টিতে তার চেয়ে কম মাত্রার হচ্ছে সেসব ছবি তোলা, যা অঙ্গ-সৌষ্ঠব ও দেহসম্পন্ন হয়, সেসব প্রাণীর ছবিও যাদের প্রতি কোন সম্মান প্রদর্শন কর হয় না বটে। তবে তা বিলাসিতার প্রকাশক। এ ধরনের ছবি সম্বলিত কাপড় দ্বারা দরজা ও প্রাচীর আবৃত করা মাকরূহ ছাড়া আর কিছুই নয়।
ছ. অ-প্রাণীদের ছবি-যেমন খেজুর গাছ, নদী, জাহাজ, পাহাড়, চন্দ্র-সূর্য ইত্যাদি প্রাকৃতিক ও নৈসর্গিক দৃশ্যাবলীর ছবি বানান ও সংরক্ষণ কোনটাইতেই গুনাহ নেই যদি তা আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগী থেকে মানুষকে গাফিল করে না দেয় কিংবা নিছক বিলাসিতার প্রতীক না হয়। অন্যথায় এ ধরনের ছবি মাকরূহ।
জ. এর পরে আসে প্রতিবিম্ব রচিত ছবি-অর্থাৎ ফটোর কথা। তা মূলতঃ মুবাহ- যদি তার মূলে কোন হারাম কাজ লক্ষ্য হয়ে না থাকে যেমন যে ব্যক্তির ছবি তার ধর্মীয় পবিত্রতা বা বৈষয়িক সম্মান প্রদর্শনমূলক। বিশেষ করে সে ব্যক্তি যদি কাফির হয়- যদি সে মূর্তি পূজারী হয় বা কমিউনিস্ট কিংবা পথভ্রষ্ট কোন শিল্পী, তাহলে তা জায়েয নয়।
ঝ. আর সর্বশেষ কথা এই যে, হারাম প্রতিকৃতি ও ছবি বিকৃত করে দেয়া হলে কিংবা অসম্মানিত ও হীন বানিয়ে দেয়া হলে তা হারামের তালিকা থেকে খারিজ হয়ে হালাল পর্যায়ে গণ্য হয়ে যায়। যেমন বিছানার চাদরে বা মেঝেতে অংকিত চিত্র, যা পা জুতা দিয়ে দলিত করা হয় ইত্যাদি।
বিনা প্রয়োজনে কুকুর পালা
নবী করীম (সা) বিনা প্রয়োজনে ঘরে কুকুর পালতে নিষেধ করেছেন।
দুনিয়ার এমন কুরুচিসম্পন্ন লোকের অভাব নেই, যারা কুকুর লালন-পালনে দু’হাতে অর্থব্যয় করে; কিন্তু মানব সন্তানের জন্যে এক ক্রান্তি ব্যয় করতেও কার্পণ্য ও কুণ্ঠা দেখায়। অনেকে আবার কুকুরের মান-অভিমান রক্ষার জন্যে অর্থ ব্যয় করেই ক্ষেন্ত হয় না, তার সাথে হৃদয়াবেগকে জড়িত করে। আর তা হয় তখন, যখন নিজের আত্মীয় স্বজনের প্রতি মনের টান অনুভব করে না এবং নিজের প্রতিবেশী ও ভাইকে ভুলে যেতে বসে (অথচ কুকুরের প্রতি এক বিন্দু উপেক্ষা সহ্য হয় না)।
মুসলমানের ঘরে কুকুর স্থান পেলে আশংকা হয়, তা খাবার, পাত্র ইত্যাদি চেটে নাপাক করে দিতে পারে। নবী করীম (স) বলেছেনঃ (আরবী**********************)
কুকুর কারো পাত্রে মুখ দিলে সেটাতে সাতবার ধুতে হবে- একবার অবশ্যই মাটি দিয়ে মাজতে হবে।
কোন কোন বিশেষজ্ঞ বলেছেন, ঘরে কুকুর পালা নিষেধ এজন্যে যে, তা অতিথি-আগন্তককে দেখলেই ঘেউ ঘেউ করে ওঠে। ভিখারীকে ভয় পাইয়ে দেয় এবং পথিককে কামড়াতেও কসুর করে না।
নবী করীম (স) বলেছেনঃ (আরবী**********************)
আমার কাছে হযরত জিবরাঈল (আ) এসে বললেনঃ আমি গত রাতে আপনার কাছে এসেছিলাম; কিন্তু ধরে প্রবেশ করিনি এজন্যে যে, দরজায় একটা প্রতিকৃতি ছিল, ঘরে ছবি সম্বলিত পর্দা ছিল, এ ছাড়া ঘরে কুকুরও ছিল। এক্ষণে আপনি ঘরের প্রতিকৃতিটির মাথাটি কেটে ফেলার আদেশ করুন, তাহলে ওটা গাছের আকৃতি ধারণ করবে, আর পর্দার কাপড়টি কেটে দুটো বালিশ বানাবার হুকুম দিন, যা দিনরাত দলিত হতে থাকবে এবং কুকুরটি বহিষ্কার করে দিন।
এখানে যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তা এই বিনা প্রয়োজনে রক্ষিত কুকুর সম্পর্কে।
শিকার ও পাহারাদারির জন্যে কুকুর রাখা
যে কুকুর কোন প্রয়োজনে পালা হবে- যেমন শিকারী কুকুর এবং ক্ষেত-খামার বা গৃহপালিত পশুর রক্ষণাবেক্ষণ ও পাহারাদারীর জন্যে পালিত কুকুর- তা এই নিষেধ-নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত নয়। রাসূলে করীম (সা) বলেছেনঃ (আরবরী***************)
শিকার বা ক্ষেত-খামার, বাড়ি বা পশু পাহারাদারির উদ্দেশ্য ছাড়া যে লোক কুকুর লালন করবে ও রাখবে, প্রতিদিন তার নেক আমল থেকে এক কীরাত পরিমাণ লাঘব হতে থাকবে।
কোন কোন ফিকাহবীদ এই হাদীস থেকে কুকুর রাখা নিষেধ বলে যে মত প্রকাশ করেছেন, তা মাকরূহ মাত্র, হারাম নয়। কেননা কুকুর পালা যদি হারাম হত তাহলে সর্বাবস্থায়ই তা হারাম হতো এবং সব সময়ই তা বর্জন করে চলতে হতো- আমল লাঘব হোক আর না হোক।
ঘর-বাড়িতে কুকুর পালতে যে নিষেধ করা হয়েছে, তার অর্থ এই নয় যে, তার প্রতি নির্মমতা অবলম্বিত হবে কিংবা তাদের নির্মূল করা বা নিধন করার জন্য এই আদেশ নয়। কেনান নবী করীম (সা) বলেছেনঃ (আরবী********************)
কুকুর যদি আল্লাহর সৃষ্ট একটি প্রজাতি না হতো যেমন আরও অনেক প্রজাতি রয়েছে, তাহলে আমি তা হত্যা করার নির্দেশ দিতাম।
রাসূলে করীম (সা) এ কথাটি দ্বারা উপরিউক্ত গুরুত্বপূর্ণ মতেরই সমর্থন দিয়েছেন। আর প্রকৃত ও বড় সত্য হল, খোদ কুরআন মজীদই এ দিকে ইঙ্গিত করে বলেছেঃ (আরবী************************)
পৃথিবীতে বিচরণশীল যত জন্তু আছে এবং যত পাখি, তার দুই ডানায় ভর করে উড়ে বেড়ায়, ওরা সবাই তোমাদের মতো ভিন্ন ভিন্নভাবে সৃষ্ট এক-একটা প্রজাতি। (সুরা আন’আমঃ৩৮)
নবী করীম (সা) তাঁর সাহাবীদের সম্মুখে এক ব্যক্তির কাহিনী বর্ণনা করেছেন। লোকটি মরূভূমির মধ্যে একটি কুকুর দেখতে পেল। কুকুরটি হাপাচ্ছিল ও পিপাসার তাড়নায় মাটি চাটছিল। লোকটি তা দেখে কুপের নিকট গিয়ে বালতি ভরে পানি তুলল ও কুকুরটিকে পানি খাইয়ে পরিতৃপ্ত করে দিল। আল্লাহ তা’আলা তার এই কাজকে কবুল করলেন এবং তার গুনাহ মাফ করে দিলেন।
আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে কুকুর পালন
আমরা এমন ধরনের লোক দেখতে পাই, যারা পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রেমে অন্ধ হয়ে নিজেদের দয়ার্দ্র হৃদয়, উচ্চ মানবতাবাদী ও সর্বজীবে দয়াশীল মনে করে। তারা ইসলামের দৃষ্টিকোণ সম্পর্কে আপত্তি উত্থাপন করে এই বলে যে, তাতে এমন বুদ্ধিমান, বন্ধুসুলভ ও বিশ্বস্ত জন্তু থেকে বিরত থাকতে বলা হলো কি করে? এ ধরনের লোকদের গোচরে আমরা এ জার্মান মনীষীর লিখিত ও জার্মানীর এ পত্রিকায় প্রকাশিত একটি রচনা পেশ করতে চাই। এই রচনায় কুকুর পালা কুকুরের সংস্পর্শ গ্রহণের দরুন যে সব বিবাদ অবশ্যম্ভাবী, তা ব্যক্ত করা হয়েছে। রচনাটি এইঃ
বিগত কয়েক বছরে লোকদের কুকুর পালনের আগ্রহ খুব বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। এ কারণে এর পরিণামে কি বিপদ ঘটতে পারে সেদিকে লোকদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করা একান্ত ই জরুরী মনে হচ্ছে। বিশেষ করে যখন লোকেরা শুধু কুকুর পালন করেই ক্ষান্ত হয় না, তার সাথে খেলা করে, তাকে চুম্বন করে। উপরন্তু কুকুর এমনভাবে মুক্ত করে দেয়া হয় যে, ছোট বড় সকলেরই হাত চাটে। অনেক সময় উদ্বৃত্ত খাবার নিজেদের পাত্রে বা থালায় করেই কুকুরের সামনে ধরে দেয়া হয়। এছাড়া এ অভ্যাস এতই খারাপ যে, সুস্থ বিবেক ও সরুচি তা গ্রহণ করতে প্রস্তুত হয় না। তা পরিচ্ছন্নতার নিয়ম-কানুনেরও পরিপন্থী।
স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে বিচার করলে কুকুর পালা ও তার সথে হাস্যরসকরণে যে বিপদ মানুষের স্বাস্থ্য ও জীবনের ওপর ঘনীভূত হয়ে আসতে পারে, তাকে সামান্য ও নগন্য মনে করা কিছুতেই উচিত হতে পারে না। অনেক লোক নিজের অজ্ঞতার খুব ভারী মাশুল দিতে বাধ্য হয়। তার কারণ এই যে, কুকুরের দেহে এমন এমন জীবানু রয়েছে যা এমন রোগ সৃষ্টি করতে পারে, যা স্থায়ী এবং যা চিকিৎসা করে সারান যায় না। কত লোক যে এই রোগে আক্রান্ত হয়ে জীবন দিতে বাধ্য হয় তা গুণে শেষ করা যায় না।
এ জীবাণুর আকৃতি ফিতার ন্যায়। তা মানবদেহে ফোঁড়া-পাঁচড়ার ন্যায় রোগ সৃষ্টি করে। এ ধরনের জীবাণু গৃহপালিত পশু ও বিশেষ করে শূকরের দেহেও পাওযা যায়; কিন্তু লালিত-পালিত হয়ে বড় হওয়ার গুণ কেবল কুকুর দেহের জীবানূরই রয়েছে।
শকুন ও শৃগালের দেহেও জীবানু থাকে। তবে বিড়ালের দেহে বড় একটা দেখা যায় না। এই জীবাণু অন্যান্য ফিতা-আকৃতির জীবানু থেকে ভিন্ন প্রকৃতির হয়ে থাকে। তা এতই সূক্ষ্ম ও সরু হয় যে, দেখাই যায় না। এ সম্পর্কে বিগত কয়েক মাসের মধ্যে কিছু তথ্য জানা গেছে।
প্রবন্ধ রচয়িতা পরে লিখেছেনঃ
এসব জীবানূ মানুষের কলিজায় প্রবেশ করে। আর তথায় নানাভাবে আত্মপ্রকাশ করে। তা অনেক সময় ফুসফুসে, ডিম্ব, তিল্লি, গুর্দা ও মস্তকের ভিতরে প্রবেশ করে। তখন এগুলোর আকৃতি অনেকটা পরিবর্তিত হয়ে যায়। এমন অবস্থা দেখা দেয় যে, বিশেষজ্ঞগণও তা ধরতে ও চিনতে অক্ষম হয়ে পড়েন।
সে যাই হোক, এ জীবানুর দরুন যে ক্ষতের সৃষ্টি হয়, তা দেহের যে অংশেই হোক না কেন, স্বাস্থ্যের পক্ষে খুবই ক্ষতিকর ও মারাত্মক। এসব জীবাণুর কোন চিকিৎসা আজ পর্যন্ত জানা যায় নি। এ করনে চিকিৎসা-অযোগ্য রোগের মুকাবিলা করার জন্যে আমাদের পূর্ণ শক্তিতে চেষ্টা করতে হবে। এ বিপদ থেকে মানুষকে বাঁচাতে হবে।
জার্মান চিকিৎসাবিদ নুললর বলেছেন , কুকুরের জীবণুর দরুন মানব দেহে যে ক্ষতের সৃষ্টি হয়, তার সংখ্যা শতকরা এক-এর কম নয় কিছুতেই। আর কোন কোন দেশে শতকরা বারো পর্যন্ত এ রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে। এ রোগের প্রতিরোধ করার সর্বোত্তম প্রন্থা হচ্ছে, এ জীবনুগুলোকে কুকুর দেহ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ করে রাখা, তাকে ছড়িয়ে পড়তে না দেয়া।.....
মানুষ যদি নিজের স্বাস্থ্য রক্ষা করতে ও জীবন বাঁচিয়ে রাখতে ইচ্ছুক হয়, তাহলে কুকুরের সঙ্গে গলাগলি ও চুমাচুমি করা পরিহার করতে হবে। তাকে নিকটে ঘেষতে দেয়া যাবে না, বাচ্চাদের তা থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে হবে। কুকুরকে তখন নিজেদের হাত চাটতে দেয়া উচিত হবে না। বাচ্চাদের খেলা, বেড়ান ও আনন্দ স্ফূর্তি করার স্থানে কুকুরকে থাকতে দেয়া ও তথায় ময়লা ছড়াবার সুযোগ দেয়া চলবে না। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, ছেলে মেয়েদের খেলার জায়গাতেই খুব বেশি সংখ্যক কুকুর থাকতে দেখা যায়।
কুকুরের খাবার পাত্র সম্পর্ণ ভিন্ন ও স্বতন্ত্র হওয়া আবশ্যক। মানুষ নিজেদের খাবারের জন্যে যেসব পাত্র ব্যবহার করে, সেসব কুকুরকে চাটবার জন্যে দেয়া খুবই অনুচিত। সেগুলোকে হাটে-বাজারে ও হোটেলে-রান্নাঘরে প্রবেশ করতে দেয়া উচিত নয়। মোটকথা, কুকুরের ব্যাপারে সতর্কতাবলম্বন করে পানাহারের সব কিছু থেকে ওদের সরিয়ে রাখতে হবে।
একজন বিধর্মী চিন্তাবিদের এ চিন্তামূলক বর্ণনা সম্মুখে রেখে বিবেচনা করে দেখা আবশ্যক যে, হযরত মুহাম্মাদ (সা) যে কুকুরের সাথে ঘনিষ্ঠ মেলামেশা করতে নিষেধ করেছেন, তা কতখানি বাস্তব ভিত্তিক এবং একান্তই বিজ্ঞানসম্মত। পানাহার সংক্রন্ত পাত্রগুলোতে কুকুর যাতে মুখ লাগাতে না পারে, সেজন্য বিশেষ সতর্কতা অবলম্বনেরও নির্দেশ দিয়েছেন। উপরন্তু বিনা প্রয়োজনে কুকুর পালতেও নিষেধ করেছেন। উপরিউক্ত বিবরণের আলোকে চিন্তা করলে রাসূলে করীম (সা) এর দেয়া বিধানে বিশ্বমানবতার জন্যে যে কি বিরাট কল্যাণ নিহিত রয়েছে তা সুস্পষ্ট অনুধাবন করা যায়।
বস্তুত নবী করীম (সা) ছিলেন একজন উম্মী। কিন্তু তা সত্ত্বে তাঁর উপস্থাপিত শিক্ষা এ কালের- এ চৌদ্দশত বছর পরে অতি আধুনিক বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও তথ্যের সাথে যে কতখানি সামঞ্জস্যপূর্ণ তা দেখলেই বিস্ময়াভিভূত হতে হয়। এ সত্য দেখার সাথে সাথে আমাদের কণ্ঠে স্বতঃ স্ফূর্তভাবে কুরআন মজীদের এ ঘোষণা ধ্বনিত হয়ে উঠেঃ (আরবী***************)
নবী নিজের ইচ্ছামত কিছুই বলেন না, যা বলেন তা ওহী ভিন্ন আর কিছু নয়।
উপার্জন ও পেশা
(আরবী****************)
সেই আল্লাহই তোমাদের জন্যে জমিনকে নম্র-মসৃন বিনীত বানিয়েছেন। অতএব তোমরা তা স্কন্ধসমূহে চল এবং আল্লাহর রিযিক আহার কর।
উপার্জন পর্যায়ে এ হচ্ছে আল্লাহর মৌলিক হেদায়েত। আর তার জন্যে জমিনকে আল্লাহ তা’আলা মানুষের খেদমতের জন্যে নিয়োজিত করেছেন। কাজেই এ নিয়ামত পুরোপুরি কাজে লাগাতে হবে এবং তার পরতে পরতে চেষ্টা ও সাধনা নিয়োজিত করতে হবে। আল্লাহর অনুগ্রহের দান পাওয়ার সন্ধানে।
কর্মক্ষম ব্যক্তির নিষ্কর্মা বসে থাকা হারাম
কোন মুসলমান ইবাদত-বন্দেগীতে নিমগ্ন হওয়ার বা আল্লাহর ওপর নির্ভরতার নাম করে রিযক উপার্জন থেকে বিরত বা বেপরোয়া হয়ে থাকবে তা কিছুতেই হতে পারে না। কেননা আকাশ থেকে স্বর্ণ রৌপ্যের বর্ষণ হবার নয়।
অনুরূপ ভাবে লোকদের দান-সাদকার ওপর নির্ভরশীল হয়ে বসে থাকা এবং জীবিকা উপার্জনের উপায়-উপকরণ হস্তগত হওয়া সত্ত্বেও তা ব্যবহার করে উপার্জনে আত্মনিয়োগ না করা এ পন্থায় নিজের ও নিজ আত্মীয়-স্বজনের প্রয়োজনাবলী পূরণ করতে চেষ্টা না করা কোনক্রমেই জায়েয হতে পারে না। এ পর্যায়ে রাসূলে করীম (সা) বলেছেনঃ
(আরবী*********************)
দান-খয়রাত গ্রহণ করা কোন ধনী লোকদের জন্যে জায়েয নয়, শক্তিমান ও সুস্থ্য ব্যক্তির জন্যেও নয়।
কোন মুসলিম অপর কারো সম্মুখে ভিক্ষার হাত প্রসারিত করবে যার ফলে তার চেহারার ঔজ্জ্বল্য বিলীন হয়ে যাবে এবং স্বীয় মনুষ্যত্বের মান-মর্যাদা অকারণ ক্ষতিগ্রস্ত করবে, নবী করীম (সা) এ ব্যাপারে কঠিন ও কঠোর বাণী উচ্চারণ করেছেন। তিনি বলেছেনঃ (আরবী*****************)
যে ব্যক্তি বিনা প্রয়োজনে ভিক্ষা চায়, সে নিজ হস্তে অঙ্গার অকত্রিত করার মতো ভয়াবহ কাজ করে। (বায়হাকী, ইবনে খাযিমাহ)
তিনি আরও বলেছেনঃ (আরবী***************************)
যে লোক ধনী হওয়ার উদ্দেশ্যে লোকদের কাছে ভিক্ষা চাইবে, সে নিজের চেহারাকে কিয়ামত পর্যন্ত সময়ের জন্যে ক্ষতযুক্ত করে দিল, সে জাহান্নামের গরম পাথর ভক্ষণ করতে বাধ্য হবে। এখানে যার ইচ্ছা নিজের জন্যে এসব জিনিস বেশি পরিমাণে সংগ্রহ করুক, আর যার ইচ্ছা কম করুক। (তিরমীযী)
তাঁর আরও একটি কথাঃ (আরবী******************)
যে ব্যক্তি নিজেকে ভিক্ষা করার কাজে অভ্যস্ত বানায়, সে আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করবে এমন অবস্থায় যে, তার মুখমণ্ডলে এক টুকরা গোশতও থাকবে না। (বুখারী, মুসলিম)
এ ভয়াবহ পরিণতি থেকে রক্ষা করার জন্যে নবী করীম (সা) মুসলমানদের ইজ্জতের হেফাযত করেছেন এবং তাদের মধ্যে আত্মসম্মান বোধ, অন্যায় কাজ থেকে নিজেকে দূরে রাখা ও ভিক্ষাবৃত্তি থেকে বিরত থাকর গুনাবলী লালনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন।
ভিক্ষাবৃত্তি জায়েয হয় কখন
কিন্তু তা সত্ত্বের নবী করীম (সা) লোকদের ঠেকা বাধার প্রতি পুরোপুরি লক্ষ্য রেখেছেন। কোন লোক যদি ভিক্ষা চাইতে ও সরকার বা ব্যক্তিদের কাছে সাহায্য চাইতে বাধ্যই হয়, তাহলে অবশ্য গুনাহ হবে না। নবী করীম (সা) ইরশাদ
(আরবী********************)
ভিক্ষা চাওয়া যখম করার সমার্থক। যে ব্যক্তি ভিক্ষা করে সে স্বীয় মুখমণ্ডলকে ক্ষতবিক্ষত করে। কাজেই যার ইচ্ছা নিজের মুখমণ্ডলকে সে অবস্থায় রেখে দিক, আর যার ইচ্ছা সে তা ত্যাগ করুক। তবে কেউ যদি কোন বর্তৃত্বসম্পন্ন ব্যক্তির কাছে ভিক্ষা চায় কিংবা এমন কোন ব্যাপারে চাইতে হয় যা একান্তই অপরিহার্য, তাহলে সে কথা স্বতন্ত্র। (আবূদাউদ, নিসায়ী)
আবু বাশার কুবাইসা ইবনুল মাখারিক (রা) বলেনঃ
(আরবী*************************)
আমি এক ব্যাপারে জামানতের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলাম। এ কারণে আমি রাসূলে করীম (সা) এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে ভিক্ষা চাইলাম। তিনি বললেনঃ অপেক্ষা কর, সাদকার মাল এসে যাবে, তা থেকে তোমাকে দিইয়ে দেব। পরে বললেন, হে কাবাইসা, ভিক্ষা চাওয়া জায়েয নয় তিন ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারো পক্ষে। একজন, যে কারো জন্যে জামানতের দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। তার জন্যে ভিক্ষা চাওয়া জায়েয যতক্ষণ না প্রার্থিত পরিমাণ মাল সে পাবে। তারপর তার বিরত হয়ে যাওয়া উচিত। দ্বিতীয় ব্যক্তি যার ধন-মাল কোন বিপদে পড়ার কারনে ধ্বংস হয়ে গেছে। সে ব্যক্তি ভিক্ষা করতে পারে, যতদিনে তার জীবনযাত্রা চালানর ব্যবস্থা না হয়। আর তৃতীয় ব্যক্তি হচ্ছে সে অনশনের সম্মখীন হয়ে যায়, যতক্ষণ তার পাড়ার তিনজন সমঝদার লোক বলে দেবে যে, লোকটি অনশনগ্রস্ত। এরূপ অবস্থায় তার পক্ষে ভিক্ষা চাওয়া জায়েয, যতক্ষণ না জীবনযাত্রা চালানর ব্যবস্থা হয়ে যায়।
এতদ্ব্যতীত যে ব্যক্তিই ভিক্ষা করে, তার জন্যে এ মাল হারামের, যা সে ভক্ষণ করে।
শ্রম সম্মানজনক
লোকেরা কোন কাজকে হীন জ্ঞান করে। কিন্তু নবী করীম (সা) তা সমর্থন করে নি। তিনি তাঁর সাহাবীদের শিক্ষা দিয়েছেন যে, যে কোন কাজই হোক-না-কেন, তাতেই সম্মান ও পরিপূর্ণ ইযযত নিহিত রয়েছে এবং লোকদের সাহায্য গ্রহণে ও তাঁর ওপর নির্ভরতায়ই রয়েছে সর্বপ্রকারের যিল্লাতি ও অপমান। তিনি বলেছেনঃ (আরবী*********************)
কোন ব্যক্তির রশি নিয়ে জঙ্গলে যাওয়া ও নিজের মাথায় কাষ্ঠের বোঝা বহন করে নিয়ে আসা ও তার বিক্রয় করে উপার্জন করা- যার ফলে আল্লাহ তাঁর ইযযতের সংরক্ষন করে দেবেন- লোকদের কাছে ভিক্ষা চাওয়ার তুলনায় অনেক ভাল ও কল্যাণময়- লোকেরা তাকে দেবে কিনা দেবে তারও কোন নিশ্চয়তা যখন নেই।
অতএব মুসলমান ব্যক্তির উচিত কৃষি, ব্যবসা, শিল্প ও এ ধরনের যে কোন কাজ বা চাকরি করে উপার্জন করা- যতক্ষণ না তা হারাম কাজে জড়িত হয়ে পড়ার মতো কোন কাজ হবে।
কৃষিকার্য দ্বারা উপার্জন
কুরআন মাজীদ আল্লাহ তা‘আলা মানুষের প্রতি স্বীয় ও অনুগ্রহের উল্লেখ প্রসঙ্গে কৃষিকার্য সংক্রান্ত বহু নীতিগতভাবে জরুরী হেদায়েত দিয়েচছন।
পৃথিবীর মাটি ও জমিকে আল্লাহ তা‘আলা উৎপাদন ও ফসল ফলানর কাজ করার যোগ্য বানিয়ে দিয়েছেন। তাকে বানিয়েছেন শয্যা, মেঝে, তা সৃষ্টির জন্যে আল্লাহর বড় একটা নিয়ামত। এনিয়ামতের কথা স্বরণ রাখা ও তার মূল্য বোঝা একান্তই কর্তব্য।
ইরশদ হয়েছেঃ (আরবী***********)
আল্লাহ তা‘আলা তোমাদের জন্যে জমিকে শয্যা ও মেঝে বানিয়েছেন, যেন তোমারা তার ওপর অবস্থিত উন্মুক্ত পথঘাটে চলাচল করতে পার। (সূরা নূহঃ১৯-২০
জমিকে তিনি সৃষ্টিকুলের জন্যে বানিয়েছেন। তাতে ফল, খেজুর গাছ, আবরণধারী, শস্য-ভূষিসহ ও ফুল রয়েছে সুগন্ধিযুক্ত। তাহলে তোমারা তোমাদের আল্লহর কুদরতের কোন কোন অবদানকে অস্বীকার করবে?
বৃষ্টিরূপে তিনি পানি বষণ করেছেন এবং দা খাল-ঝর্ণয় প্রবাহিত করেছেন আর তার সাহায্যে তিনি মৃত জমিকে জীবিত করেন।
(আরবী************)
তিনি ঊর্ধ্ধলোক থেকে পানি বর্ষণ করেছেন। পরে তার সাহায্যে সর্বপ্রকারের উদ্ভিদ, গাছপালা ইত্যাদি উৎপাদন করেছি, পরে তাতে সবুজ-শ্যামল-তাজা শাখা-প্রশাখা বের করেছি- তা থেকেই আমারা স্তরসম্পন্ন দানা বের করি।
(আরবী **************
মানুষের কর্তব্য তার খাদ্যের প্রতি দৃষ্টি দেয়া- চিন্তা করা। আমারাই প্রয়োজনমত পানি বর্ষণ করেছি। পরে জমি বিস্ময়করভাবে দীর্ণ করেছি আর তাতে শস্য, আঙ্গুর ও তরিতরকারী উৎপাদন করেছি।
বাতাসকে আল্লাহ্ সুসংবাদদাতা করে পাঠিয়ে থাকেন। তার সাহায্যে মেঘমালঅ চলাচল করে এবং উুদ্ভিদসমূহ ফলাধারী হয়।
(আরবী***************)
আর জমিকে বিস্তীর্ণ বানিয়েছি, তাতে সংস্থাপিত করেছি উচু শক্ত পর্বতমালা এবং তাতে প্রতিটি জিনিস সুপরিকল্পিত ও পরিমিতভাবে উৎপাদিত করেছি। আর আমারা তোমাদের জীবিকা তাতেই বানিয়েছি তাদের জন্যেও, যাদের তোমারা রিয্কদাতা নও। আর প্রতিটি জিনিসেরই সম্ভার-স্তপ আমাদের কাছে সংরক্ষিত, একটা জ্ঞাত পরিমাণেই আমারা তা থেকে প্রদান করে থাকি। বাতাসকে আমারা ফল ভারাক্রান্ত করেই পাঠিয়ে থাকি। পরে ঊর্ধ্ধলোক থেকে পানি বর্ষণ করি আর তোমাদেরে সিক্ত করি তা দিয়ে। নতুন তোমারা তো আর সমাহার সঞ্চয় করে রাখতে পারতে না। (সুরা হিজরঃ১৯-২২)
এ সব কটি আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা কৃষিকাজে নিয়ামত ও তার সহজ সাধ্যতার উপয়-উপকরণের দিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। রাসূলে কারীম (স) বলেছেনঃ (আরবী**********)
যে মুসলমানই কোন গাছ লাগায় বা ক্ষেত করে আর তা থেকে পাখি বা মানুষ যা খায়, তা তার জন্যে দান হয়ে যায়। (বুখার, মুসলিম)
অর্থাৎ তার এই কাজের সওয়াব অব্যাহতভাবে হতে তাকে, যতদিন সেই গাছ বা ক্ষেত থেকে খাওয়ার কাজ চলতে থাকে। যদিও জমির মালিক বা বৃক্ষ রোপনকারী মরেই গিয়ে থাক না কেন কিংবা তার মালিকানা হস্তান্তরিতই হোক না কেন
বিশেষজ্ঞগণের মতে আল্লাহর দয়া ও দানশীলতার পক্ষে এটা অসম্ভব নয় যে, তিনি এরূপ ব্যাক্তিকে তার মৃত্যুর পরও সওয়াব দান করতে থাকবেন যেমন করে তার জীবদ্দশায় তাকে দিচ্ছিলেন। সাদকায়ে জারিয়া, এমন ইলম, যার দ্বারা লোকেরা উপকৃত হয় কিংবা নেক-বখ্ত সন্তান, যে তার জন্যে দো‘আ করতে থাকে অথবা কোন রোপিত বৃক্ষ, কৃষি এবং সীমান্ত প্রহরা –এই ছয়টি কাজ সম্পর্কেই উপরিউক্ত াথা প্রযোজ্য।
হাদীমে উদ্ধৃত হয়েছে, েএক ব্যক্তি হযরত আবুদ্দারদা (রাঃ) এর কাছে উপস্থিত হলো। তখন তিনি আখরোটের চারা রোপন করছেন, ওটাতে ফল ধরতে তো অনেক বছর লেগে যাবে?....জাবাবে আবুদ্দারদা (রাঃ) বললেনঃতাতে ক্ষতি কি?অন্যরা খাবে আর আমি তার সওয়াব কামাই করব?
নবী করীম (স) -এর অপর এক সাহাবী থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেনঃআমি আমার কান দিয়ে রাসূলে কারীম (স) কে বলতে শুনেছিঃ (আরবী ***************)
যে ব্যাক্তি কোন গাছ লাগায়, তার পরে তার হেফাযত ও দেখাশোনা করতে থাকে, যতদিন না সে গাছে ফল ধরে, এই সময়ে সে ফলের যা কিছু ক্ষুতি সাধিত হবে, তার সওয়াব সে আল্লাহর কাছ থেকে পাবে।
এ সমস্ত এবং এ ধরনের আরও বহু হাদীসকে ভিক্তি করে বিশেষজ্ঞগণ বলেছেন যে, কৃষিকাজ উপার্জনের অপরাপর উপায়ের তুলনায় অনেক উত্তম। কিন্তু অপর কিছু বিশেষজ্ঞের মতে শিল্প ও হতের কাজ অনেক ভাল। আবার কাহারও কাহারও মতে ব্যবসাই উওম উপায়।
অপর কিছু বিশেষজ্ঞ বলেছেন, বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন কাজ উত্তম বিবেচিত হতে পারে, যেমন খাদ্যের তীব্র অভাব হলে কৃষিকার্য উত্তম । কেননা তার কল্যাণ সাধরণভাবে সকলেরই প্রাপ্য। আর যখন ডাকাত পড়ার কারণে হাটে-বাজারে কম মালের আমদানী হয়, তখন ব্যবসা ভাল কাজ আর শিল্পজাত দ্রব্যদির প্রয়োজন পূরণে শিল্পকর্ম উত্তম বিবেচিত হবে। (আরবী******************)
এই শেষে উল্লিথিদ বিবরণ আধুনিক অর্থনৈতিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে পুরোপুরিভাবে সঙ্গতিপূর্ণ।
হারাম কৃষিকার্য
ইসলাম যে সব উদ্ভিদ খাওয়া হারাম হারাম ঘোষণা করেছে কিংবা যার ব্যবহার ক্ষতিকর, তার চাষাবাদও হারাম। যেমন গাজাঁ, আফিম ইত্যাদি।
তামাক সম্পর্কেও এ কথা। তবে তা হারাম যাঁরা মনে করেন, তামাক খাওয়া হারাম তাদের মতে। অনেকে এ মতটাকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। আর যাদের মতে তামাক খাওয়া মাকরূহ, তাদের মতে তার চাষাবাদও মাকরূহ।
অমুসলিমদের কাছে বিক্রয় করে অর্থ পাওয়া যাবে- এ উদ্দেশ্যে কোন হারাম জিনিসেন চাষাবাদ করা মুসলমানের পক্ষে জায়েয নয়। মুসলমান হারাম জিনিসেন প্রচলন করার কাজ কখনই করতে পারে না। তাই শূকর লালন-পালন করা ওঅমুসলমান খৃস্টান প্রভৃতির নিকট বিক্রয় করার উদ্দেশ্যে- মুসলমানদের জন্যে জায়েয নয়। আমরা পূর্বেই বলেছি ইসলামের দৃষ্টিতে হালাল আঙুর এমন ব্যক্তির কাছে বিক্রয় করা জায়েয নয়, যে তা দিয়ে সুরা (মদ) বানাবে বলে জানা যাবে।
শিল্প ইত্যাদি
ইসলম কৃষিকর্মের উৎসাহ দিয়েছে। তার সৌর্ন্দর বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছে। এ কাজে বিপুল সওয়াব হওয়ার কথাও কলে দিয়েছে। কিন্তু মুসলিম মিল্লাতের লোকেরা কেবল কৃষিকর্মে মগ্ন হয়ে থাকবে- যেমন ঝিনুকের পোকা (sea sell) ঝিনুকের মধ্যেই বন্দী থাকে- তা আদৌ পছন্দনীয় নয়। শুধু কৃষিকার্যকে যথেষ্ট মনে করা ও চাষের গরুর পিছনে পিছনে চলতে থাকাকে ইসলাম মুসলমানদের জন্যে পছন্দ করে না। কেননা তাই যদি হয় তাহলে সম্ভাব্য জাতীয় বিপদ-আপদের মুকাবিলা করা তাদের পক্ষে সম্ভবপর হবে না। এ কারণে নবী করীম (স) যদি কৃষিকাজরক লাঞ্ছনার কাজ বলে থাকেন, তাহলে তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। কেননা কালের কাস্তবতা সেই কথার সত্যতা প্রকট করে তুলেছে। তিনি বলেনঃ (আরবী***********************)
তোমরা যদি সুদভিত্তিক বেচা-কেনার কাজ কর ও গরু-মহিষের লেজুর ধরেই পড়ে থাক, জিহাদে মনোযোগ না দিয়ে কৃষিকার্য়য মগ্ন হয়ে থাক, তাহলে আল্লাহ তোমাদের ওপর লাঞ্ছনা চাপিয়ে দেবেন। পরে তা দূর করা যাবে না যতক্ষণ না তোমারা তোমাদের দ্বীনের প্রতি প্রত্যাবর্তন করবে । (আবূ দাউদ) এ কারণে কৃষি কার্য়ের সঙ্গে শিল্প-পেশার কাজ করাও জরুরী । এসবের সাহায্যেই সচ্ছল-স্বচ্ছন্দ জীবনের প্রয়োজন এবং একটি স্বাধীন ও শক্তিশালী উম্মত-ৈএকটি সুদৃঢ় ও স্বয়ংসম্পূর্ণ সরকার ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার দাবিসমূহ পূরণ হতে পারে। শিল্প পেশা ইসলারে দৃষ্টিতে একটা বৈধ কাজ-ই নয়-যেমন কোন কোন আলিম ও ই, া, কলেছেন- তা ফরযে কিফায়াও অর্থাৎ মুসলিম সমাজে সর্ব প্রকারের শিল্প ব্যবসায়ে পারদর্শী এত বেশি লোকের বর্তমান থাকা আবশ্যক যেন জাতীয় প্রয়োজন পূণে হতে কোন অসুবিধাই না হয় ও তার নিজের যাবতীয় কাজ সুসম্পন্ন করা তার পক্ষে সম্ভব হয়। শিল্প পেশার কোন দিক যদি এমন অনটন দেখা দেয় যে, সে কাজ করার লোকই পাওয়া যায় না, তাহলে গোটা সমাজ ও জাতীই সেজন্যে দোষী ও গুনাহগার হবে-বিশেষ করে নেতৃবৃন্দ ও রাষ্ট্র পরিচালকবৃন্দ সেজন্যে দায়ী হবে।
ইমাম গাজালী (র) বলেছেনঃ
সেসব জ্ঞান অর্জনই ফরযে কিফায়া, যা ছাড়া মানুষের বৈষয়িক জীবন চলতে পারে না। যেমন চিকিৎসা বিদ্যা, দেহের সুস্থতা রক্ষা জন্যে তা একান্তই জরুরী। অংক বা হিসাববিদ্যা, পারস্পরিক লেন-দেন, অসীয়ত ও মীরাস বন্টনসহ যাবতীয় কাজে তা অপরিহার্য। সে সব বিদ্যা-এমন যে, তা জারা-লোক বর্তমান না থাকলে জনগণক কঠিন অসুবিধার সন্মুখীন হতে হয়। আর কেউ যখন এ ধরনের কাজে লেগে যায়, তখন অন্যরা এ কাজের দায়িত্ব থেকে মুক্তি লাভ করে। এ কারণে আমাদের মতে চিকিৎসা ও হিসাববিদ্যা ফরযে কিফায়া। বনেদী ধরনের কাজ ও শিল্পও ফরযে কিফায়া ছাড়া আর কিছু নয়। যেমন জমি চাষাবাদ, হালচষ, কাপড় বুনন, পশু পালন ইত্যাদি। ক্ষের কার্য ও দর্জীকর্ম করাও এ ফরয়ে কিফায়াই। কোন দেশে এসবের ব্যবস্থা না থাকলে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়া কিছুতেই জায়েয হতে পারে না। আরবী****************)
কুরআন মজীদে বহু প্রকারের শিল্পকর্মের প্রুত ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে এবং সেগুলো যে দুনিয়ার মানুষের প্রতি আল্লহর বড় নিয়ামত, তা স্পষ্ট করে বলা হয়েছেঃযেমন হযরত দাঊদ (আ) সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ ইসলামে হালাল-হারামের বিধান (আরবী*******************)
আমার তার জন্যে লোহাকে নরম করে দিয়েছি, নির্দেশ দিয়েছি, বর্ম তৈয়ার করা এবং তার কড়াগুলো ঠিক পরিমাণ মতো বানাও। (সূরা সবাঃ১০-১১)
আর আমারা তাকে বর্ম য়ৈার করার শিল্পবিদ্যা শিক্ষা দিয়েছিলাম, যেন তা যুদ্ধে তোমাদের প্রতিরক্ষা করতে পারে। তাহলে তোমারা কি শোকর আদয় করবে? (সূরা আম্বিয়াঃ৮০)
হযরত সুলায়মান (আ) সম্পর্কে বলা হয়েছে।
আর আমরা তার জন্যে তামার ঘর্ণা প্রবাহিত করেছি এবং এমন জ্বিন তার অধীন করে দিয়েছি যারা তাদের আল্লাহর নির্দেশে তার সন্মুখে কাজ করত।
আর আমরা তার জন্যে তামার ঘর্ণা প্রবাহিত করেছি এবং এমন জ্বিন তার অধীনে করে দিয়েছি যারা তাদের আল্লাহর নির্দেশে তার সন্মুখে কাজ করত। তাদের মধ্যে যে যে আমার নির্দেশ অমান্য করত, তাকে আমারা জ্বলন্ত অগ্নিকুন্ডুলির আযাবের স্বাদ আস্বাদ করাতাম!তারা তার (সুলায়মানের ) জন্য যা সে চাইত, নির্মাণ করত, উঁচু উঁচু প্রাসাদ ইমারত, প্রতিষ্ঠিত ডেগসমূহ। হে দাউদ বংশধরেরা!শোরক আদায়কারী হিসেবে কাজ কর।
কুরআনের যুল-কারনাইনের সুউচ্চ সুদৃঢ় প্রাচীর নির্মাণেরও উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছেঃ (আরবী *********************)
আমার রব্ব আমাকে যা কিছু দিয়েছেন তা অনেক। তোমারা শুধু শ্রম-মেহনত করেই আমরা সাহায্য করা। আমি তোমাদের ও তাদের মাঝখানে বাঁধ বেঁধে দেব। আমাকে লোহার চাদর এনে দাওে। শেষে দুটো পর্বতের মধ্যকার শূণ্যতাকে সে যখন ভরাট করে দিল, তখন লোকদের বলল, এখন আগুন জ্বালাও। যখন এই অগ্নি-প্রাচীর আগুনের মতো সম্পূর্ণ লাল বর্ণ ধারণ করল, তখন সে বলল, আনো এখানে আমি তার ওপর গলিত তামা ঢেলে দেব। এ বাঁধটি এতই দৃঢ় বানান হয়েছিল যে, ইয়াজুজ-মাজুজ তার ওপর চড়েও আমতে পারত না, আর তার মধ্যে সুরঙ্গ রচনাও তাদের জন্যে আরো কঠিন ছিল। (সূরা কাহাফঃ৯৫-৯৭)
হযরত নূহের নৌকা নির্মাণের কাহিনীও কুরআনে উদ্ধৃত হয়েছে। তাতে এক সুদৃঢ় জাহাজ নির্মাণের ইশারা বিধৃত, যা নদী সমুদ্রে পাহড়ের মতো উন্নত হয়ে জলতে সমক্ষম। বলা হয়েছেঃ (আরবী*************)
নদী-সমূদ্রের বুকে পর্বতের ন্যায় মাথা উঁচু করে চলমান জাহাজগুলো আল্লাহরই নিদর্শন বিশেষ। (সূরা শূরাঃ৩২)
কুরআনের বহু সংখ্যক সূরায় সর্বপ্রকারের শিকার-বিদ্যা ও কার্য়ের**** উল্লেখ হয়েছে। যেমন মৎস্য শিকার, সামুদ্রিক জন্ত শিকার, স্থলভাগের জন্ত শিকার এবং মণি-মুক্তা আহরণের উদ্দেশ্যে ডুবুরি দ্যিা ইত্যাদি।
সর্বোপরি কুরআন মাজীদ লোহার সঠিক মূল্য ও কর্যাকারিতার উল্লেখ হয়েছে।
তার পূর্বের কোন ধর্মগ্রন্থ বা মানবরচিত গ্রন্থেও তার উল্লেখ পাওয়া যায়না। কুনআনে রাসূল প্রেরণ ও কিতাব নাযিল করণের উল্লেখ করার পর বলা হয়েছেঃ (আরবী************************)
এবং আমরা লোহা সৃষ্টি করেছি। তাতে কঠিন শক্তি নিহিত রয়েছে এবং আছে জনগণের অশেষ অসীম কল্যাণ।
এ আয়াতটি যে সূরা‘লৌহ’। এ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, লৌহ শিল্পের ওপর ইসলাম বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে।
বস্তত ইসলামের দৃষ্টিতে মানব সমাজের প্রয়োজন পূরণ ও প্রকৃত কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে যে শিল্পকর্মই করা হবে , তা-ই‘আমলে সালেহ’-নেক আমল বিবেচিত হবে। যদি সে কাজে সত্যিই আন্তরিকতা রক্ষা করা হয় এবং যেরূপ নৈপূণ্য ও দক্ষতা অবলম্বন করতে ইসলাম নির্দেশ দিয়েছে, তা পুরোমাত্রায় অবলম্বিত হয়।
মানব সমাজে অত্যন্ত হীন ও নগণ্য বিবেচিত কত শিল্প-পোশাকে ইসলাম অত্যন্ত মর্যাদাবান বানিয়েছে। যেমন ছাগল চরানর রাখালকে লোকেরা সন্মানের চোখে দেখত না। কিন্ত নবী করীস (স) বলেছেনঃ (আরবী**************)
আল্লাগর প্রেরিদ প্রত্যেক নবীই ছাগল চরিয়েছেন। সাহাবিগণ জিজ্ঞেসা করলেনঃ (আরবী***********)
হে রাসুল! আপনিও কি ছাগল চরিয়েছেন?
সাহাবিগণ জিজ্ঞেস করলেনঃ (আরবী**************)
হে রাসূল!আপনিও কি ছাগল চরিয়েছেন?
জবাবে তিনি বললেনঃ (আরবী***************)
হ্যা, আমি মজুরীর বিনিময়ে মক্কার লোকদের ছাগল চরিয়েছ। (বুখারী)
খতামুন্নবীয়ীন হযরত মুহাম্মাদ (স) ছাগল চরিয়েছেন। বড় কথা, সে ছাগল তাঁর নিজের ছিলনা। বরং তা ছিল মক্কার লোকদের এবং তিনি তা নির্দিষ্ট পরিমাণ মজুরীর বিনিময়ে চরিয়েছিলেন। এ কথার উল্লেখ করে নবী করীম (স) তাঁর সাহাবীদের শিক্ষা দিচ্ছিলেন যে, যারা কাজ করে –কাজ করে উপার্জন করে, তাদেরই গৌরব । যারা নিষ্কর্ম বসে থাকে ও উপার্জনহীন থেকে লোকদের ওপর দিয়ে খায়, তাদের কোন গৌরব বা মর্যাদা নেই।
কুরআন মজীদে হযরত ঈসা (আ) -এর কিসসা উদ্ধৃত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, তিনি একজন বৃদ্ধ শায়খের কাছে শ্রমিক হিসেবে ক্রমাগত আটটি বছর পর্যন্ত কাজ করেছেন। তার এ শ্রমের মজুরী ছিল, বৃদ্ধের কন্যাদের একজনকে তাঁর কাছে বিয়ে দেয়া। হযরত ঈসা (আ) তার কছে খুবই ভাল শ্রমিক বলে গণ্য হচ্ছিলেন, খুবই বিশ্বস্ত কর্মী ছিলেন তিনি। বৃদ্ধের এক কন্যা অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তা সহকারে বলেছিলঃআরবী (******************)
হে পিতা, তুমি ওকে শ্রমিক হিসেবে মজুীরীর বিনিময়ে ঠিক করে রাখ। নিজের রাখা কর্মচারী উত্তম তো সে-ই হতে পারে, যে শক্তিশালী এবং বিশ্বস্ত।
হযরত ইবনে আবাস (রা) বর্ণনা করেছেন, হযরত দাউদ বর্ম ও তৈজসপত্র নির্মাতা ছিলেন। হযরত আদম ছিলেন জমি চাষকারী। হযরত নূহ (আ) ছিলেন মিস্ত্রী, হযরত ইদরীস (আ) ছিলেন দর্জী এবং হযরত মূসা (আ) ছিলেন ছাগলের রাখাল।
অতএব মুসলমান যে কোন হালাল পেশা গ্রহণ করে সন্তষ্ট থাকতে পারে। প্রত্যেক নবীই কোন-না কোন পেশা অবশ্যই অবলম্বন করতেন। সহীহ হাদীসে বলা হয়েছে। (আরবী*****************)
নিজের শ্রমের বিনিময়ে উপার্জিত খাদ্যের তুলনায় উওম খাবার কেউ খেতে পারে না । আর আল্লাহর নবী দাউদ (আ) শ্রম করেই উপার্জন করতেন ও খাবার জোটাতেন। (বুখারী)
নিষিদ্ধ কজ ও পেশা
তবে কিছু কিছু কাজ ও পেশা ইসলাম মুসলমানদের জন্যে হারাম ঘোষণা করেছে। কেননা এসব কাজ ও পেশা লোকদের আকীদা, বিশ্বাস , চরিত্র, মান-সন্মন ও সাংস্কৃতিক মূল্যমানকে বয়ানকভাব ধ্বংস ও ক্ষতিগ্রস্ত করে।
বেশ্যাবৃত্তি
বেশ্যাবৃত্তি একটা পেশা হিসেবে পাশ্চত্যের ও পাশ্চাত্যানুসারী অনেকগুলো দেশেই স্বকৃত ও সমর্থিত। এজন্যে রীতিমত অনুমতি ও লাইসেন্স দেয়া হয়, দেয়া হয় অবাধ নির্বিরোধ সুযোগ-সুবিধা। এই বৃত্তিটিকেও দেশ চলতি অন্যান্য পেশার মতো একটা পেশার মর্যাদা দেয়া হয় এবং এ পেশা সংক্রান্ত যাবতীয় অধিকার দান করা হয়।
কিন্তু ইসলাম এ পেশার ওপর কুঠোরাঘাত করেছে এবং স্বাধীনা কিংবা ক্রীতদাস কোন রমণীকেই স্বীয় স্ত্রী-অঙ্গের দ্বার কোনরূপ উপার্জন করার অনুমতি দেয়নি।
জাহিলিয়াতের যুগে কেউ কেউ তার ক্রীতদাসীর ওপর দৈনিক হারে ‘কর’ ধার্য করত। এ ‘কর’ তাদের মালিকদের রীতেমত আদায় করে দিতে তারা বাধ্য ছিল। সেজন্যে তাঁকে যে কোন উপায়েই হোক উপার্জন করতে হতো। এ কারণে অনেক দাসীই ধার্যকৃত ‘কর’ আদায়ের নিমিত্তে বেশ্যাবৃত্তি করতে বাধ্য হতো। অনেক দাসী-মালিক আবার সরাসরি দাসীকে এ কাজে নিয়োজিত করত। আর তার বিনিময়ে সে মোটা পরিমাণ উপর্জন করত। উত্তরকালে ইসলাম এসে নারীদের এ চরম দুর্দশা ও জঘন্য কজকর্মের বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্তি দান করে। এ সময়ই আল্লাহর ফরমান নাযিল হয়ঃ (আরবী)
তোমারা তোমাদের দাসী বা কন্যদের বেশ্যাবৃত্তি করতে বাধ্য করনা- ওরা তো পবিত্রতা ও সতীত্ব রক্ষা করে থাকতে চায়-শুধু এজন্যে যে, এরা মাধ্যমে তোমরা বৈষয়িক স্বার্থ লাভ করবে। (সূরা আন-নূরঃ৩৩)
হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেছেনঃমুনাফিক প্রধান আবদুল্লাহ ইবনে উবাই রাসূলে করীম (স) -এর কাছে উপস্থিত হলো। তার সাথে ছিল ‘মুয়াযত’ নাম্নী এক অনিন্দ্যসুন্দরী দাসী। সে বললঃইয়া রাসূল!এই মেয়েটি অমুক ইয়াতীমের মালিকানাধীন দাসী। আপনি কি ওকে বেশ্যাবৃত্তি করার অনুমতী দেবেন?তাহলে সে ইয়াতীমরা অনেক মুনাফা লাভ করতে পারত। নবী করীম (স) জবাবে স্পষ্ট ভাষায় বললেনঃ‘না’।
নবী করীম (স) এই বীভৎস পেশার পথ চিরতরে বন্ধ করে দিলেন, তার রোজগারে যারই কোন ফায়দা হোক, বড় কোন প্রয়োজনই পূরণ হোক এবং বহু বড় মহৎ উদ্দেশ্যেই হোক-না কেন , ইসলামী সমাজকে সর্ব প্রকারের পাপ কার্জের পংকিলতা থেকে মুক্ত ও পবিত্র রাখই ইসলামের লক্ষ্য।
নৃত্য ও যৌন শিল্পকর্ম
ইসলাম যৌন উত্তেজক নৃত্য পেশা হিসেবে গ্রহণ করা আদৌ সমর্থন করে না। অনুরূপভাবে এমন কাজেও ইসলামে অনুমোদন নেই, যা মন-মেজাজে যৌন উত্তেজনা বৃদ্ধি করে। অশ্লীল গান, নির্লজ্জ অভিনয় এবং এ ধরনের অন্যান্য অর্থহীন কাজকর্ম এ পর্যায়ে পড়ে। বর্তমান কালে একে যদিও Art বা শিল্পকলা-এ লোভনীয় নামে অভিহিত করা হয় এবং তাকে উন্নতি-অগ্রগতি লাভের জন্যে অপরিহার্য মনে করা হয় কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিতে তা চরম শুমরাহী ভিন্ন আর কিছুই নয়।
বস্তুত বৈবাহিক সম্পর্ক ভিন্ন অন্য কোনভাবেই নারী-পুরুষের যৌন সম্পর্ক ইসলামে সম্পূর্ণ হারাম ঘোষিত হয়েছে। যেসব কথা ও কাজ এ পথ উন্মুক্ত করে দেয়, ইসলামের দৃষ্টিতে তা সবাই সম্পূর্ণ হারাম। কুরআন জ্বেনা-ব্যভিচার হারাম ঘোষণার জন্যে যে মুজিযাপূর্ণ পদ্ধতি অবলম্বন করেছে, তাতেই এই তত্ত্ব নিহিত।
কুরআনের ঘোষণা হচ্ছেঃ (আরবী*****************)
জ্বেনা-ব্যভিচারের নিকটেও ঘেঁষবে না। কেননা তা অত্যন্ত নির্লজ্জতার কাজ এবং খুবই কদর্য পথ ও উপায়া। (সূরা বনী-ইসরাইলঃ৩২০)
ওপরে আমরা যা যা বলেছি, উপরন্ত যেসব কথাকে লোকেরা যৌন উত্তেজক মনে করে, তা সবাই এ ব্যভিচারের নিকটবর্তী করে দেয়ার উপকরণ। বরং তা-ই মনুষকে সেদিকে উদ্ধুদ্ধ করে, তার প্রতি আকর্ষণ তীব্র করে তোলে। কজেই এ পর্যয়ে যত কাজ আছে তা যারা করে তারা খুবই মারাত্নক কাচ করে, তাতে সন্তেহ নেই।
ভস্কর্য, প্রতিকৃতি ও ক্রুশ নির্মাণ মিল্প
ইসলামে প্রতিকৃতি হারাম। উপরে বিস্তারিতভাবে তার বিশ্লেষণ দেয়া হয়েছ। প্রতিকৃতি নির্মাণ আরো কঠিনভাবে হারাম। বুখারী শরীফে উদ্ধৃত হয়েছে, সায়ীদ ইবনুল হাসান বলেনঃ (আরবী****************)
আমি ইবনে আব্বাস (রা) -এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। এ সময় এক ব্যক্তি এল। বললঃহে ইবনে আব্বাস!হতের কারিগরিই আমার জীবিকার উপায়। আমি এ ধরনের ছবি তৈরী করি। ইবনে আব্বস (রা) বললেনঃআমি স্বয়ং রাসূলে করীম (স) -কে যা বলতে শুনেছি, তোমাকে আমি ঠিক তাই শোরাব। আমি তাঁকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি ছবি বা প্রতিকৃতি নির্মাণ করবে তাতে রূহ দেয়ার শাস্তি আল্লাহ তাকে দেবেন, কিন্তু সে তাতে রূহ কখনই দিতে পারবে না। এ কথা শুনে প্রতিক্রিয়ায় লোকটির মুখমন্ডল বিকৃত ও ম্লান হয়ে গেল। ইবনে আব্বাস তাকে বললেনঃতুমি যদি ছবি বা প্রতিকৃতি বানাতেই চও, তাহলে গাছ ইত্যাদি নিষ্প্রাণ জিনিসের ছবি বানাও। (বুখারী)
মূর্তি, ক্রুশ-এধরনের সব জিনিস সম্পর্কে এ একই বিধান প্রযোজ্য।
তবে ফটোগ্রাফীর ছবি সম্পর্কে তো আমারা পূর্বেই বলেছি যে, শরীয়তের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ দৃষ্টিকোণ হচ্ছে, তা জায়েয। আর খুব বেশি বললে মাকরূহই বলা যায়। তবে শর্ত এই যে, সেই কাজটা মূলতঃকোন হরাম উদ্দেশ্যে হতে পারবে না। যেমন নারীর যৌন আকর্ষণমূলক অঙ্গসমূহকে উলঙ্গ করে তোলা, নারী-পুরুষের জুম্বনরত অবস্থায় ছবি এবং যেসবের বড়ত্ব বা পবিত্রতা প্রতিষ্ঠা করা হয়, সেমবের ছবি তোলা-যেমন ফেরেশতা, নবী-রসূল ইত্যাদির ছবি।
মাদক ও জ্ঞান-বুদ্ধির বিনষ্টকারী দ্রব্যাদি দশিল্প
পূর্বেই বলা হয়েছে, মাদক-মদ্য প্রচলনে যে কোন রকমের অংশগ্রহণ বা সাহায্য সহযোগিতাকে ইসলাম হারাম ঘোষণা করেছে। তা বানান-প্রস্তুত করণ, বন্টন বা পান করা-করান, সবই সম্পূ্র্ণরূপে নিষিদ্ধ। যে লোকই এ কাজ করবে, সে-ই রাসূলের ভাষায় অভিশপ্ত।
হাশীশও আফিমের ন্যায় বিবেক-বুদ্ধি বিলোপকারী যাবতীয় দ্রব্যাদি মাদক দ্রবের মতই হারামি। এসব জিনিসের লেন-দেন, ক্রয়-বিক্রয়, বিলি –বন্টনও তার উৎপাদন শিল্প-সবই হারাম। মুসলমানের পক্ষে এমন কোন শিল্পকর্ম বা পেশা অবলম্বন করা যা হারাম কাজের ওপর ভিত্তিশীল কিংবা যারা দ্বারা কোন হারাম কাজের প্রচলন ঘটে ইসলামের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ অপছন্দনীয়, অবাঞ্ছনীয়।
ব্যবসা করে উপার্জন করা
ইসলাম কুরআনী ঘোষণা ও রাসূলের সুন্নাতের মাধ্যমে ব্যবসা করার ওপর খুব বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছে এবং তা করার জন্যে বলিষ্ঠ আহবান জানিয়েছে। এ উদ্দেশ্যে বিদেশ সফরের জন্যেও উৎসাহ দিয়েছে এবং তাকে আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান বলেছে। ওপরন্ত ব্যবসায়ের জন্যে যারা বিদেশ সফর করে তাদের উল্লেখ করা হয়েছে আল্লাহর পথে জিহাদকারী লোকদের সাথে। বলা হয়েছেঃ (আরবী********************)
কিছু লোক আল্লাহর অনুগ্রহের সন্ধানে বিদেশ সফর করবে এবং অপর কিছু লোক আল্লাহর পথে যুদ্ধ-জিহাদ করবে। (সূরা মুজাম্মিলঃ২০)
আন্তর্জাতিক ব্যবসার জন্যে সামুদ্রিক যোগাযোগ ও যাতায়াত পথ অত্যন্ত গুরুত্বপূ্র্ণ। এ পথই মানুষে ও জাতিসূহের জন্যে অভ্যন্তরীন ও বৈদেশিক বাণিজ্যের অবাধ সুযোগ করে দিয়েছে। এ ব্যাপরটাকে আল্লাহ ত‘আলা মনুষের প্রতি তাঁর এক বিশেষ অনুগ্রহের অবাদান বলে উল্লেখ করেছেন। সমুদ্র নিয়ন্ত্রণ ও অনুকূল বানান ও জাহাজ চালানর সুযোগ দানের অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করে আল্লাহ ত‘আলা নিজেই বলেছেনঃ (আরবী******************)
আর তোমারা দেখতে পা্ও, নদী-সমুদ্রে নৌকা-জহাজ পানির বক্ষ দীর্ণ করে চলাচল করছে, যেন তোমরা তাঁর অনুগ্রহের সন্ধান করতে পার একং তাঁর শোকর আদায় করতে পর। (সূর ফাতিরঃ১২)
কোন কোন আয়াতে সেই সাথে বাতাস চালাবার কথাও বলা হয়েছেঃ (আরবী*******************)
তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে এটাও যে, তিনি বাতাসসমূহকে সুসংবাদ দেয়ার ও তোমাদেরকে তাঁর রহমতের সাথে পরিচিতকরণের জন্যে পাঠান এবং এজন্যেও যে, নৌকা-জাহাজগুলো তাঁর নির্দেশে চলতে পারে এবং তোমরা তাঁর অনুগ্রহের সন্ধান করতে ও কার শোকর আদায় করতে পার।
আাল্লাহ তা‘আলা মক্কায় লোকদের প্রতি অনুগ্রহ করে তাদের জন্যে এমন সব ব্যবস্থা কর্যকর করে দিয়েছেন যে, তাদের নগর মক্কা সমগ্র আরব উপদ্বীপের মধ্যে একটি বিশেষ ও বিশিষ্ট ধরনের ব্যবসা কেন্দ্র হয়ে গিয়েছিল। হযরত ইবরাহীম (আ) দো‘আ করেছিলেনঃ (আরবী*******************)
অতএব হে আল্লাহ!তুমি লোকদের মনকে তাদের প্রতি আগ্রহী বানিয়ে দাও এবং তাদের রিযক দাও নানা প্রকারের ফলমুল দিয়ে, যেন তারা শোকর করতে পারে।
এ দো‘আও মক্কাবাসীদের জন্যে খুবই কল্যাণকর প্রমাণিত হয়েছে। অনুরুপভাবে কুরাইশদের প্রতিও আল্লাহ তা‘আলা অনুগ্রহ করেছিলেন ইয়েমেনমুখী শীতকালীন ব্যবসায়ী সফর এবং সিরিয়ামুখী গ্রীষ্মকালীন ব্যবসায়ী সফরে সুষ্ঠু ও নিরাপদ ব্যবস্থা করে দিয়ে। আর তাদের এ সফরকালীন নিরাপত্তা ছিল আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ এবং তা করা হয়েছিল এজন্যে যে, তারা কাবা ঘরের খেদমতে আঞ্জাম দিত। আতএব তদের উচিত একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করে তাঁর এ অনুগ্রহের শোকর আদায় করা। কেননা তিনিই কাবা ঘরের একমাত্র রব্ব একমাত্র অনুগ্রহকারী আল্লাহ। (আরবী******************)
যেহেতু কুরাইশরা অভ্যস্ত হয়েছে অর্থাৎ শীতকালীন ও গ্রীষ্মকালীন বিদেশ সফরে তাদের অভ্যাস রয়েছে। অতএব তাদের কর্তব্য এ ঘরে আল্লাহর ইবাদত করা, যিনি তাদের ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্যে খেতে দিয়েছেন এবং সকল প্রকারের ভয়-ভীতি থেকে নিরাপত্তা দান করেছেন। (সূরা কুরাইশ)
ইসলাম মুসলমানকে আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ী লেন-দেন ও যাতায়াত-যোগাযোগের বিরাট সুযোগ করে দিয়েছে। প্রত্যেক বছর হজ্জের সময় এ সুযোগ আসে। আল্লাহ তা‘আলা স্পষ্ট ভাষায় এ হজ্জকালীন সফরের কথা উল্লেখ করে বলেছেনঃ (আরবী***************)
আযাতে উল্লিথিত ‘কল্যাণকর ব্যবস্থাসূহের ‘মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা হচ্ছে ব্যবসা। কিন্তু মুসলমানরা হজ্জের সময় ব্যবসা করতে কুষ্ঠবোধ করত। তারা মনে করত, হজ্জের সময় ব্যবসা করলে হজ্জের খলেস নিয়তে দোষ প্রবেশ করবে এবং তাদের ইবদতের পরিচ্ছন্নতা ও নিষ্কলুষতা বিনষ্ট হবে। এ পর্যয়ে কুরআন মজীদে স্পষ্ট ভাষায় বলে দেয়া হয়েছেঃ (আরবী****************)
তোমারা যদি হজ্জকালে তোমাদের আল্লাহর কাছ থেকে অনুগ্রহ পেতে চাও, তবে তাতে তোমাদের কোন দোষ হবে না। (সূরা বাকারাঃ১৯৮)
যে সব লোক মসজিদে বসে সতাল সন্ধা আল্লাহর তসবীহ জপে কুরআন মজীদ তদের উদ্দেশ্য করে বলেছেঃ (আরবী********************)
এমন বহু লোক রয়েছে, ব্যবসা বা নগদ বেচা-কেনা যাদের আল্লাহর যিকির নামায কয়েম করা ও যাকাত দেয়ার দ্বীনী কজ-কর্ম থেকে ভুলিয়ে রাখতে পারে না। (সূরা আন-নূরঃ৩৭)
এর অর্থ কুরআনের দৃষ্টিতে মুসলমান মসজিদের মধ্যে বন্দী হয়ে থাকা লোক হতে পারে না। নয় তারা দরবেশ, পরনির্ভশীল বা দুনিয়া ত্যাগী-সন্ন্যাসী বা বৈরাগী। অনুরূপভাবে তারা দুনিয়ার কাজে একান্তভাবে মশগুল হয়ে যাওয়া লোকও নয়। আসলে তারা হচ্ছে কজের লোক। আর তাদের বিশেষত্ব হচ্ছে, তদের বৈষয়িক কজ দ্বীনী, অনুরূপভাবে তারা দুনিয়ার কজে একান্তভাবে মশগুল হয়ে যাওয়া লোকও নয়। আসলে তারা হচ্ছে কাজের লোক্। আর তদের বিশেষত্ব হচ্ছে, তাদের বৈষয়িক কাজ দ্বীনী দায়িত্ব পালন থেকে তদের বিরত ও বিস্মৃত করে রাখতে পারে না।
কুরআন মজীদে ব্যবসা সংক্রান্ত কথাবার্তার কিয়দাংশ আমরা উপরে তুলে ধরলাম।
এরপর সুন্নত ও হা্দীসের কথা। নবী করীম (স) নিজে ব্যবসায়ের কজের জন্যে বিপুলভাবে উৎসাহ দান করেছেন। এ ব্যাপারটি তাঁর কছে ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি নিজে কথা ও কাজ দ্বারা এ কাজের ভিত্তি সুদৃঢ় করে দিয়েছেন।
এ পর্যায়ে তাঁরা গুরুত্বপূর্ণ কথাসমূহের মধ্য থেকে কুতিপয় নীতিকথা এখানে উল্লেখ করছিঃ (আরবী**************)
বিশ্বস্ত সত্যাশ্রয়ী ব্যবসায়ী কিয়ামতের দিন শহীদদের সাথে অবস্থান করবে। (আরবী***********)
সততা পরায়ণ বিশ্বস্ত ব্যবসায়ী নবী স্বয়ং সিদ্দীক ও শহীদদের সঙ্গী হবেন।
নবী করীম (স) ব্যবসায়ীদের মুজাহিদ ও আল্লাহর পথে শাহাদত বরণকারীদের সমান মর্যাদায় উল্লেখ করেছেন দেখেও আমাদের মনে কোন বিস্ময়ের উদ্রেক হয় না। কেননা, জীবনের অভিজ্ঞতা আমাদের সামনে প্রমাণ করেছে যে, জিহাদ কেবলমাত্র যুদ্ধের ময়দানেই অনুষ্ঠিত হয় না। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও এই জিহাদ অবশ্যম্ভাবী।
রাসূলে করীম (স) ওয়াদা করেছেন, ব্যসায়ীরা আল্লাহর কাছে এ উচ্চ মর্যাদা লাভ করবে এবং পরকালে তাদের জন্যে হবে এই অশেষ সওয়াব। কেননা, ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে প্রায়ই লোভ ও লালসার দাসত্ব হতে দেখা যায়। যে কোন উপায়ে মুনাফা লুন্ঠনের প্রবনতা খুবই প্রকট হয়ে থাকে এ ক্ষেত্রে । আর ধন ধন সৃষ্টি করে, মুনাফা আরও মুনাফা লাভের জন্যে মানুষকে প্ররোচিত করে। কিন্তু যে ব্যবসায়ী সততা ন্যায়পরায়ণতা ও বিশ্বস্ততা রক্ষা করে, সে তো জিহাদকারী ব্যক্তি। সে প্রতিনিয়ত লোভ-লালসার সাথে মুকাবিলা করে চলছে। অতএব মুজাহিদের মর্যাদা তার জন্যে খুবই শোভনীয় এবং বাঞ্ছনীয়।
ব্যবসায়ের ধর্ম হচ্ছে, তা মানুষকে ধন-দৌলতের স্তুপে ডুবিয়ে দেয়। সে দিন-রাত মূলধন ও মুনাফার হিসেব করতেই নিমগ্ন হয়ে থাকে। এমন কি আমরা দেখতে পাচ্ছি, নবী করীম (স) মিম্বরের ওপর দাঁড়িয়ে খোতবা দিচ্ছেন, এমন সময় একটি ব্যবসায়ী কফেলা পণ্য –দ্রব্য-সম্ভার নিয়ে তথায় উপস্থিত হয়। লোকেরা এই কফেলার পৌছার খবর পাওয়ার সাথে সাথে রাসূলের খোতবার প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে সেদিকে দৌড়ে গেল। এ প্রক্ষিতেই কুরআন মজীদের নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল হয়। (আরবী***************)
ওরা যখন কোন ব্যবসা বা আনন্দানুষ্ঠান দেখে দখন ওরা সেদিকেই দৌড়ে যায় এবং হে নবী তোমাকে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় ফেলে যায়। যা কিছু আল্লাহর কাছে রেয়ছে তা এ আনন্দানষ্ঠান ও ব্যবসা অপেক্ষা অনেক ভালো ও কল্যাণময় এবং আল্লাহই হচ্ছে সর্বত্তম রিযিকদাতা। (সূরা জুমা‘আঃ১১)
কাজেই যে লোক এ ঘর্ণাবর্তে পড়েও দৃঢ় ঈমানদার ও প্রত্যয়শীল, আল্লাহর ভয়ে ভরপুর অন্তর ও আল্লাহর যিকিরে সিক্ত হয়ে থকতে পারে, সে তো নিঃসন্দেহে আল্লহর নিয়ামত প্রাপ্ত নবী, সিদ্দীক ও শহীদদের মধ্যে গণ্য হবে।
ব্যবসার ব্যাপারে আমাদের পথ-প্রদর্শনের জন্যে রাসূলে করীম (স) -এর কর্মনীতিই যথেষ্ট। তিনি যেমন আধ্যাত্মিক দিকের প্রতি পূর্ণ মাত্রায় গুরুত্বারোপ করেছেন, তেমনি মদীনায় তাকওয়ার ও আল্লাহর সন্তাষ্টির ভিত্তিতে মসজিদও কয়েম করেছিলেন। যেন তা আল্লাহর ইবাদত, ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা ও চর্চা এবং দ্বীনী দাওয়াত প্রচারের কেন্দ্র হওয়ার সাথে সাথে রাষ্ট্র এবং সরকারেরও কেন্দ্র (Head Quarter) হতে পরে। তিনি মানুষের অর্থনৈতিক দিকের ওপরও যথাযথ গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি খালেস ইসলামী বাজার সৃষ্টি করেছিলেন, যার ওপর ইয়াহূদীদের কোন কর্তৃত্ব বা আধিপত্য চলতে পরত না। পূর্ব থেকে চলে আসা বনূ কায়নুকা বাজার ইয়াহূদীদেরই কর্তৃত্বাধীন ছিল। নবী (স) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বাজারের ব্যবস্থাপনা ও নিয়ম-কানুন নিজেই পচলন করেছিলেন এবং নিজেই সেটার দেখাসোনা করতেন। এ বাজারটির বৈশিষ্ট্য এই যে তথায় কোনরুপ ধোঁকা-প্রতারণা ঠকাঠকির করবার বা মাপে-ওজনে কোনরূপ কম-বেশি করার কিংবা পণ্যদ্রব্য আটক করে লোকদের কষ্ট দেয়ার কোন সুযোগই ছিল না।
এ সবের সাথে সাথে আমার লক্ষ্য করছি, সাসূলে করীমের সাহাবিগণের মধ্যে সুবিজ্ঞ ব্যবসায়ী, সুদক্ষ কারিগর, কৃষক এবং সামাজিক জীবনের প্রয়োজনীয় সকল কাজ ও বিদ্যার দক্ষতাসম্পন্ন ও পেশাবলম্বনকারী লোক রয়েছেন।
রাসূলে করীম (স) লোকদের মধ্যে বসবাস করতেন। দাঁর ওপর আল্লাহর ফরমান – কুরআনের আয়াত নাযিল হতো। লোকদের মধ্যে তিনি তা পাঠ করে শোনাতেন। জিবরাঈল (আ) সকল-সন্ধ্যা ওহী নিয়ে তাঁর কাছে আসতেন।
সাহবিগণের অবস্থা ছিল এই যে, তাঁরা রাসূলে করীম (স) থেকে এক মুহূর্তের তররেও বিচ্ছিন্ন হওয়া পছন্দ করতেন না। এসব সত্ত্বের আমরা দেখি, মসস্ত সাহাবী নিজ নিজ কাজ ও পেশায় মগ্ন রয়েছেন। কেউ হয়ত ব্যবসায়ী সফর করেছেন, কেউ নিজের খেজুরের বাগান নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। আাবার কেউ কেউ নিজের পেশা ও কারিগরি কাজ থেকে নিয়ে মশগুল থাকার দরুন রাসূলে করীমের কাছে উপস্থিত হয়ে দ্বীন শেখার কাজ থেকে বঞ্চিত থাকছেন। ফলে তিনি কাঁর অপর এক ভাই –যিনি রাসূলের দরবারে উপস্থিত থাকতে পেরেছিলেন-থেকে সব কিছু জেনে নিচ্ছেন। এটা তাঁদের কর্তব্যও ছিল। কেননা রাসূলে করীম (স) স্থায়ী নীতি হিসাবে ঘোষণা করে দিয়েছিলেনঃ (আরবী*****************)
উপস্থিত লোক যেন অনুপস্থিত ব্যক্তির কাছে সবকিছু পৌছে দেয়।
অধিকাংশ আনসার কৃষিকাজে রত থাকতেন। আর মুহাজিররা সাধারণতঃব্যবসায়ী ছিলেন। আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা) মুহাজির ছিলেন। তাঁর কর্মনীতি আমাদের সন্মুখে চিরভাস্বর হয়ে আছে। তাঁর দ্বীনী ভাই সা‘দ ইবনে আনসারী তাঁকে কাঁর অর্ধেক সম্পদ, তাঁর দুটি বাড়ির একটি এবং দুই স্ত্রীর মধ্য থেকে একজন স্ত্রীকে তালাক দিয়ে তাঁর কাছে বিবাহ দেয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন।
তিনি সা‘দ (রা) -কে বললেনঃ (আরবী*****************)
আল্লাহ আপনার ধন-মাল ও পরিবার-পরিজনে বরকত দিন। আমার ওসবের কোন প্রয়োজন হবে না। এখন ব্যবসা করার মতো কোন বাজার থাকলে আমাকে দেখিযে দিন, আমি ব্যবসা করব।
সা‘দ বললেন, হ্যাঁ, বনু কায়নুকার বাজার রয়েছে তো! পরের দিন তিনি পনির ও ঘি সহ বাজারে চলে গেলেন ও বিক্রি করেন। তিনি এ ব্যাবসা চলিয়ে প্রচুর সম্পদ উপার্জন করেন। , মৃত্যুকলে তিনি এক বিপুল বৈভব রেখে গিয়েছিলেন।
হযরত আবূ বকর (রা) -এর দৃষ্টান্ত আরও ভাস্বর। তিনি বরাবর ব্যবসাই করেছেন। এজন্যে প্রানপণ খাটা-খাটুনি করতেন। এমন কি খলীফা নির্বাচিত হওয়ার দিনও তিনি বাজারে যাওয়ার ইচ্ছা করলেন।
হযরত উমর (রা) নিজের সম্পর্কে বলেনঃ (আরবী*******************)
বাজারের কেনা-বেচা আমাকে এমনভাবে মশগুল করে রেখেছিল যে, আমি রাসূলে করীম (স) -এর হাদীস শ্রবণ থেকে বঞ্চিত থেকে গেলাম।
হযরত উসমান (রা) ও অপরাপর সাহাবী সম্পর্কে এই কথা।
ব্যবসা সম্পর্কে গির্জার ভূমিকা
ইসলাম পূর্বোক্তভাবে দ্বীন ইসলামের ছায়াতলে থেকে তারা জগতিক মহাযাত্রা অব্যহত রেখেছে। ইসলামে বিশ্বাসী লোকেরা ব্যবসা ও ক্রয়-বিক্রয়ের কাজ করেছে;কিন্ত এ কাজে ব্যস্ততা ও নিমগ্নতা তাদের আল্লাহর যিকির থেকে গাফিল করেনি, আল্লাহর আনুগত্যের পথ তেকে করেনি একবিন্দু বিচ্যুত। অথচ এ সময়কালে মধ্যযুগের বড় বড় দেশ ওি খ্রিস্টন ইউরোপের রাষ্ট্রসমূহের জনগণ ব্যবসা সম্পর্কে দৃষ্টি পরস্পর-বিরোধী মতের মধ্যে দ্বিধান্বিত হয়ে পড়েছিল। একদিকে ছিল‘নিষ্কৃতির’মত। ব্যবসায়ের তৎপরতায় মশগুল হলে নফস বহু প্রকরের গুনাহের আবিলতায় পংকিল হয়ে পড়বে, কাজেই নিজেকে তা থেকে রক্ষা করতে হবে এবং সে জন্যে এ ধরনের কাজকর্ম থেকে দূরে সরে থাকতে হবে। অপরদিকে ধারণা ছির, ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের শিক্ষা ও মতের বিরুদ্ধে ব্যবসা ও শিল্পকর্মে আত্মনিয়োগ করলে মানুষ অভিশপ্ত হয়ে যাবে। কেননা এই গুনাহ কেবল একটি খারাপ কাজই নয়, তা চিরন্তন পাপ ও সর্বকালের অভিশাপ যেমন পৃথিবীতে তেমনি আকাশলোকেও; ইহকালে এবংপরকালে।
কিদ্দীস অগস্টস বলেনঃকয়-কারবার (Business) মূলতই গুনাহ। কেননা তার প্রভবে নফস বা মন মহাসত্য আল্লাহর দিক থেকে হটে যায়।
অপর একজন বলেনঃযে ব্যক্তি কোন কিছু ক্রয় করে সেই অবস্থাই সে জিনিসকে বিক্রি করার উদ্দেশ্যে, তাতে কোনরূপ পরিবর্তন আনা হয় না; তাহলে এ শেষ ব্যক্তি সেসব ক্রয়-বিক্রয়কারী গোষ্ঠীর মধ্যে শামিল হয়ে যায়, যার প্রকৃত ইবাদতের উচ্চতর ও পরিবেশ থেকে দূরে ছিটকে পড়েছে।
আসলে এসব কথাবার্তা কিদ্দীস রোলসের উপস্থাপিত শিক্ষার দীর্ঘসূত্রিতা ছাড়া আর কিছুই নয়। কিদ্দীস বলেছিলেন, কোন খ্রিস্টানেরই যেহেতু তার অপর খ্রিস্টান ভাইয়ের সাথে কোনরূপ ঝগড়া –ফাসাদে লিপ্ত হওয়া উচিত নয়, এজন্যেই খ্রিস্টনদের মধ্যে কোন ব্যবসায়ী তৎপরতা থাকাও বাঞ্ছনীয় নয়।
হারাম ব্যবসা
কিন্তু ইসলামে ব্যবসা হারাম নয়। তবে যে ব্যবসায়ে জুলুম, ধোঁকাবাজি, প্রতারণা, ঠকবাজি, মুনাফাখোরী কিংবা কোন নিষিদ্ধ জিনিসের ক্রয়-বিক্রয়, উত্পাদন হয় তা নিশ্চয়ই হারাম।
যেমন মদের ব্যবসা, বিবেক-বুদ্ধি আচ্ছন্নকারী দ্রব্যাদির ক্রয়-বিক্রয় কিংবা শূকর ব্যবসা অথবা মূর্তি, প্রতিকৃতি বা অনুরূপ ধরনের ব্যবসা নিশ্চয়ই নিষিদ্ধ। কেননা এ জিনিসগুলো গ্রহন, পান, চলাচলকরণ ও তা থেকে উপকার গ্রহণ ইসলামে সম্পূর্ণরূপে হারাম করে দেয়া হয়েছে । ইসলাম এ কাজের প্রতি কোন সমর্থন দিতে আদৌ প্রস্তুত নয়। এসব পথে যা কিছুই উপার্জন হয় তা হারাম ও জঘন্য। তা খাওয়ার ফলে ব্যক্তির দেহে যে গোশত বৃদ্ধি পাবে, তার জন্যে জাহান্নামই উপযুক্ত স্থান। যেসব লোক এ সব নিষিদ্ধ জিনিসের ব্যবসায় লিপ্ত, সে সত্যবাদী, ন্যায়পরায়ণ ও বিশ্বস্ত হবে বলে মনে করার কোন কারণই থাকতে পারে না। কেননা এসব ব্যবসায়ের ভিত্তই হচ্ছে ঘৃণ্য এবং হারাম। ইসলাম তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং এ ব্যবসাকে চালু রাখতে আদৌ প্রস্তুত নয়।
তবে স্বর্ণ বা রেশমের- রেশমী কাপড়ের ব্যবসা করা হারাম নয়। কেননা এ দুটো পুরুষদের জন্যে না হলেও নারীদের জন্যে তো হালাল। তবে এসব জিনিস দ্বারা তৈরী এমন জিনিসের কারবার- যা কেবল পুরুষরাই ব্যবহার করে, তা জায়েয হবে না।
হালাল ও জায়েয ব্যবসায়ে ব্যবসায়ীর কতগুলো কর্তব্য রয়েছে। সে কর্তব্য পালন না করলে ব্যবসায়ীকে কিয়ামতের দিন গুনাহগারদের দলভুক্ত হতে হবে। আর এ গুনাহগাররা অবশ্যই জাহান্নামে যাবে।
নবী করীম (সা) একদিন নামাযের জন্যে বের হয়ে এলেন। তিনি দেখতে পেলেন, লোকেরা কেনা-বেচা করছে। তিনি দেখতে পেলেন, লোকেরা কেনা-বেচা করছে। তিনি তাদের বললেনঃ
হে ব্যবসায়ী লোকেরা ! লোকেরা রাসূলের ডাকে সাড়া দিল। তারা সেদিকে চোখ তুলে তাকিয়ে দেখল। তখন নবী করীম (সা) বললেনঃ (আরবী**********************)
কেয়ামতের দিন ব্যবসায়ীরা মহাপাপীরূপে উত্থিত হবে। তবে তারা নয় যারা আল্লাহকে ভয় করবে, নেকভাবে সততা ও সভ্যতা সহকারে ব্যবসায়ের কাজ সম্পন্ন করবে। (তিরমিযী, ইবনে মাযাহ)
ওয়াসিলা ইবনুল আসকা (রা) বলেছেন : রাসূলে করীম (সা) আমাদের কাছে আসতেন- আমরা ছিলাম ব্যবসায়ী এবং বলতেন : (আরবী*****************)
হে ব্যবসায়ীরা, তোমরা মিথ্যা কথা ও মিথ্যা কারবার থেকে অবশ্যই দূরে সরে থাকবে।
এত এব ব্যবসায়ীদের কর্তব্য এ মিথ্যাকে সম্পূরূপে পরিহার করে চলা। কেননা ব্যবসায়ীদের জন্যে তাই হচ্ছে একটি অতি বড় বিপদ। মিথ্যাই মানুষকে পাপের পথে টেনে নিয়ে যায়। আর পাপের পথের পরিণতি হচ্ছে জাহান্নাম। তাদের খুব বেশি কিরা-কসম করাও পরিহার করা কর্তব্য। বিশেষ করে মিথ্যা কসম খাওয়া খুবই মারাত্মক। কেননা নবী করীম (সা) বলেছেন:
(আরবী*****************)
কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা’আলা তিনজনের প্রতি তাকাবেন না, তাদেরকে পবিত্রও করবেন না, তাদের জন্যে হবে পীড়াদায়ক আযাব। তাদের মধ্যে একজন হচ্ছে মিথ্যা কিরা-কসম করে যে লোক তার পণ্য বিক্রয় করে সে।
আবু সায়ীদ (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, একজন বেদুঈন একটি ছাগী নিয়ে যাচ্ছিল। আমি তাকে জিজ্ঞাস করলাম, তুমি কি ছাগীটি তিন দিরহাম বিক্রয় করবে? লোকটি বললঃ না আল্লাহ কসম। কিন্তু পরে সে সেই মূল্যেই ছাগীটি বিক্রয় করে দিল। আমি এ ব্যাপারটি রাসূলে করীম (সা) এর কাছে উল্লেখ করলাম। তিনি শুনে বললেন: (আরবী************)
লোকটি দুনিয়ার বিনিময়ে তার পরকালকে বিক্রি করে দিয়েছে।
ব্যবসায়ীর উচিত ধোঁকাবাজি ও ঠকবাজি থেকে দূরে থাকা। কেননা যে লোক ধোঁকাবাজি ও ঠকবাজি করে, সে ইসলামী উম্মতের বাইরে চলে গেছে।
ওজন ও পরিমাপে কমবেশি করা অত্যান্ত খারাপ কাজ। মুনাফাখোরী ও মজুদদারী তাকে পরিহার করে চলতে হবে। কেননা তা করলে আল্লাহ ও রাসূল তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলবেন।
সুদী কারবার করা চলবে না। কেননা সুদকে সুদী করবার লব্ধ মুনাফাকে আল্লাহ তা’আলা নির্মূল নিশ্চিহ্ন করে দেন, হাদীসে বলা হয়েছেঃ (আরবী****************)
কোন লোক যদি সুদের একটি দিরহামও জেনে শুনে খায় তবে তা ছত্রিশ বার জ্বেনা করার চাইতেও বড় গুনাহ। (আহম্মদ)
এসব বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা পরে করা হবে।
চাকরি
চাকরি করে রুজি-রোজগার করা মুসলিম মাত্রের জন্যেই জায়েয। তা সরকারী চাকরি, হোক, কোন প্রতিষ্ঠানের হোক কিংবা কোন ব্যক্তিগতভাবে করো কাছে। যতদিন সে চাকরি সংক্রান্ত যাবতীয় কাজের দায়ত্ব পালন করতে সক্ষম থাকবে, ততদিন এ চাকরি করা তার জন্যে বৈধ। কিন্তু যার মধ্যে যে কাজের যোগ্যতা নেই, তার পক্ষে সেকাজের নিয়োগ প্রার্থনা করা জায়েয নয়। বিশেষ করে প্রশাসনিক ও বিচার বিভাগীয় গুরুত্বপূর্ণ পদসমূহ সম্পর্কে এ শর্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, নবী করীম (সা) ইরশাদ করেছেনঃ (আরবী****************)
ধ্বংস প্রশাসকদের জন্যে, ধ্বংস নেতৃস্থনীয় লোকদের জন্যে, ধ্বংস কোষাধ্যক্ষদের জন্যে। কত না লোক কিয়ামতের দিন কামনা করবে, তাদের চুলের চুটি যদি সুরাইয়া তারকার সাথে বেঁধে দেয়া হতো এবং তাদের যদি আসমান ও জমিনের মধ্যে ঝুলিয়ে রাখা হতো, তবে কতই না ভাল হতো।
হযরত আবূ যর (রা) থেকে বর্ণিতঃ (আরবী***********************)
আমি বললাম, হে রাসূল! আপনি কি আমাকে কোন দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত করবেন না? এ কথা শুনে তিনি তাঁর হাত আমার কাঁধের ওপর রাখলেন এবং বললেন : হে আবু যর তুমি বড় দুর্বল ব্যক্তি। আর এ পদ হচ্ছে কঠিন আমানতের ব্যাপার। কিয়ামতের দিন তাই হবে লজ্জা ও লঞ্ছনার কারণ। কেবল সে লোক ছাড়া, যে তা পূর্ণ সততা সহকারে গ্রহণ করল এবং এ পদের যে দায়িত্ব ও কর্তব্য তার ওপর বর্তায় তা সে যথাযথ পালন করল।
নবী করীম (সা) আরও বলেছেনঃ (আরবী******************)
বিচারক তিন ধরনের। তন্মধ্যে এক ধরনের বিচারক জান্নাতে যাবে। আর অপর দুধরনের বিচারক যাবে জাহান্নামে। জান্নাতে যাবে সে বিচারক যে প্রকৃত সত্যকে জানতে পারল এবং সে অনুযায়ী ফয়সালা করল- রায় দিল। কিন্তু যে বিচারক প্রকৃত সত্য জানতে পেরে জুলুম করল, সে জাহান্নামে যাবে। আর সেও জাহান্নামে যাবে সে মূর্খতা ও অজ্ঞতার ভিত্তিতে বিচারকার্য সমাধা করল।
অতএব এসব বড় বড় দায়ত্বপূর্ণ পদের জন্যে কোনরূপ কামনা বা প্রার্থনা করা এবং তা পাওয়ার জন্যে চেষ্টা করা কোন মুসলমানেরই উচিত নয়, যদিও কোন পদের যোগ্যতা তার রয়েছে। কেননা যে ব্যক্তি কোন পদকে নিজের রব্ব বানিয়ে নেবে তার সে পদই তাকে তার গোলাম বানিয়ে নেবে। আর যে লোক পৃথিবীতে বাহ্যত প্রকাশমান ফলাফলকেই সব কিছু মনে করবে, সে আসমানী তওফীক থেকে বঞ্চিত হবে।
হযরত আবদুর রহমান ইবনে সামুরাতা (রা) বলেনঃ (আরবী****************)
রাসূলে করীম (সা) আমাকে বললেন : হে আবদুর রহমান! কোন নেতৃত্ব তুমি চাইবে না। কেননা তুমি যদি না চাইতেই পেয়ে যাও তাহলে তোমাকে সে দায়িত্ব পালনে সাহায্য করা হবে। আর যদি প্রার্থনা ও চেষ্টার ফলে তুমি পাও, তাহলে তোমাকে তারই ওপর নির্ভরশীল বানিয়ে দেয়া হবে।
হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: (আরবী*******************)
যে লোক বিচারকের পদ লাভ করার কামনা করল, তা চাইল ও সেজন্যে সুপারিশ করল, তাকে তারই হাতে সোপর্দ করে দেয়া হবে, আর কেউ যদি এ পদ গ্রহন করত বাধ্য হলো ( নিজে চাইল না) তার সাহায্যার্থে একজন ফেরেশতা আল্লাহ নাযিল করবেন। (আবু দাউদ, তিরমিযী)
এসব কথা সে পর্যায়ে প্রযোজ্য যখন শূন্যপদ পূরণের জন্যে অন্যান্য লোক মজুদ রয়েছে। পক্ষান্তরে অবস্থা যদি এই হয় যে, শুন্য পদ পূরণ করার জন্যে সে ছাড়া আর কেউ নেই এবং দেখা যাবে যে, সেই কাজের জন্যে নিজেকে পেশ না করলে সার্বিক কল্যাণই অচল হয়ে যাবে, জাতীয় কার্যাবলী বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে, তখন নিজেকে সেই কাজের জন্যে পেশ করায় কোন দোষ নেই। কুরআন মজীদ হযরত ইউসুফের কিসসা আমাদেরকে শুনিয়েছে। তাতে উল্লেখ হয়েছে যে, তিনি নিজেই বাদশাহকে বলেছিলেন : (আরবী********************)
সে বলল, রাজ্য ও রাষ্ট্রের ধন-ভণ্ডারসমূহের ওপর আমাকে কর্তৃত্বশীল করে নিযুক্ত করুন। আমি তো হেফাযত ও সংরক্ষণকারী এবং সব বিষয়ে জ্ঞানের অধিকারী।
রাজনৈতিক পদ লাভের জন্যে প্রার্থনা করা ব্যাপাটিকেও ইসলামের পথ-নির্দেশ এরূপ।
হারাম চাকরি
চাকরি করা জায়েয পর্যায়ে আমরা এ পর্যন্ত যা কিছু বললাম, তা কেবল সেসব চাকরির বেলায় যখন সে চাকরির কাজে মুসলিম জনগণের পক্ষে ক্ষতির কারণ নিহিত থাকবে না। অতএব মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত কোন সৈন্যবাহিনীর কোন পদে চাকরি করা কোন মুসলমানের পক্ষে জায়েয হতে পারে না। অনুরূপভাবে যে প্রতিষ্ঠান বা শিল্প কারখানা মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্যে অস্ত্রশস্ত্র তৈয়ার করার কাজে নিযুক্ত, তার কোন চাকরি করা মুসলমানদের জন্যে জায়েয নয়। ইসলাম ও মুসলামনদের বিরুদ্ধে প্রচার-প্রোপাগাণ্ডা চালানর প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে এ কথা।
এ রূপেই জুলুম বা হারাম কাজে সাহায্য সহায়তাকারী কোন প্রতিষ্ঠান বা সংস্থায় চাকরি গ্রহণও মুসলমানের জন্যে হারাম। যেমন কোন সুদী কারবারের প্রতিষ্ঠান, মদ্য উত্পানদের কারখানা বা মদ্য বিক্রির দোকান, কোন নৃত্যশালা, থিয়েটার, ছায়াছবি নির্মান ইত্যাদি ধরনের কাজে চাকরি গ্রহণও জায়য হতে পারে না।
এসব ক্ষেত্রে চাকরি গ্রহণকারীরা এই বলে নিষ্কৃতি পেতে পারে না যে, তারা নিজেরা তো হারাম কাজ করছে না। কেননা পূর্বেই বলেছি, ইসলামের মৌলনীতি হচ্ছে পাপ কাজের সাহায্য করাও পাপ- সে সাহায্য যে রকমেরই এবং যতটা মাত্রারই হোক না কেন। এ কারণেই নবী করীম (সা) সুদী কারবারের চুক্তি বা হিসাব লেখক এবং তার সাক্ষীদের ওপর যেমন অভিশাপ বর্ষণ করেছেন, তেমনি অভিশাপ করেছেন সুদখোরদের ওপরও। অভিশাপ করেছেন মদ্য চোলাইকারী ও মদ্য পরিবেশনাকরীর ওপর যেমন করেছেন মদ্যপের ওপর।
এ বিধান ও নির্দেশ তখনকার জন্যে, যখন এ ধরনের চাকরি বা কাজ গ্রহনের জন্যে মানুষ সাংঘাতিক অসুবিধায় পড়ে বাধ্য হবেন। কিন্তু বাস্তবিকই যদি কোন মুসলমান এরূপ অসুবিধায় পড়ে যায় এবং এ কাজ ছাড়া অন্য কোন হালাল ধরনের চাকরি না-ইপাওয়া যায়, তাহলে মনে মনে এ কাজের প্রতি ঘৃণা পোষণ সহকারে এ চাকরি নেয়া যেতে পারে। তবে এ ছাড়া হালাল কোন চাকরি পাওয়া যায় কিনা তার জন্যে অবিশ্রান্ত চেষ্টা চালাতে থাকতে হবে, যেন আল্লাহর অনুগ্রহে এ কাজ থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে পুরোপুরি হালাল কোন পেশা বা চাকরি পাওয়া সম্ভব হয় এবং হারাম উপর্জন থেকে বেঁচে যেতে পারে।
মুসলমান সব সময় সন্দেহ বা সংশয়পূর্ণ কাজ থেকে দূরে সরে থাকতে চেষ্টা করবে। কেননা তা দ্বীন পালন ও আকীদার ক্ষেত্রে দুর্বলতার সৃষ্টি করে। তাই এ কাজে বিরাট পরিমাণ উপার্জন ও প্রচুর ধন লাভ সম্ভবপর হলেও মুসলিম ব্যক্তি তা পরিহার করে চলে। নবী করীম (সা) বলেছেন : (আরবী*****************)
যা তোমাকে সংশয়ে ফেলে তা পরিহার কর এবং যা সন্দেহমুক্ত উন্মুক্ত মনে হয়, তাই গ্রহণ করো। (আহমদ, তিরমিযী, নিসায়ী)
তিনি আরো বলেছেন : (আরবী******************)
যাতে সংশয় রয়েছে তা ছেড়ে দিয়ে যাতে কোনরূপ সংশয় নেই তা যতক্ষন না গ্রহণ করবে, ততক্ষণ মানুষ মুক্তাকীদের মর্যাদা লাভ করতে পারে না। (তিরমিযী)
(অন্য কথায় দোষ থেকে বাঁচতে গিয়ে অনেক ক্ষেত্রে দোষমুক্ত জিনিসও ত্যাগ করা মুক্তাকীদের কাজ।)
উপার্জন পর্যায়ে সাধারণ নিময়
উপার্জন পর্যায়ে সাধারণ নিময় হচ্ছে, যে কোন উপায়ে যে কোন পথ ও পন্থায় ইচ্ছা উপার্জন করতে চেষ্টা করাকে ইসলাম মুসলমানদের জন্যে জায়েয করেনি। বরং ইসলাম উপার্জনের জন্যে শরীয়তসম্মত পন্থা ও শরীয়ত অসমর্থিত পন্থার মধ্যে পার্থক্য করার নির্দেশ দিয়েছে। এ নীতির মূল কথা হচ্ছে সামাজিক-সামষ্টিক কল্যান। আর এ পার্থক্যকরণের মৌলনীতি হচ্ছে যেসব পথে উপার্জন বা মুনাফা লাভ করার ক্ষেত্রে অপরের ক্ষতি অবশ্যম্ভাবী তা শরীয়তসম্মত পন্থা নয় আর যে সব পন্থায় ব্যক্তিদের পরস্পরের মধ্যে মুনাফার বন্টন হয় পারস্পরিক সন্তুষ্টি ও অনুমতির ভিত্তিতে এবং সে বন্টন হয় সুবিচারপূর্ণ, তা অবশ্যই শরীয়ত-সমর্থিত পন্থা।
আল্লাহ তা’আলা নিজেই এ মৌলনীতি ঘোষণা করেছেন কুরআনের নিম্মোদ্ধৃত আয়াতেঃ (আরবী****************)
হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা বাতিল পন্থায় তোমাদের পরস্পরের মাল ভক্ষণ করবে না। তবে পারস্পরিক সন্তুষ্টির ভিত্তিতে যদি ব্যবসা করা হয়, তাহলে গ্রহন করতে পার। তেমরা নিজেদের হত্যা করো না। কেননা আল্লাহ তোমাদের প্রতি বড়ই দয়াবান। যে লোক সীমালংঘন ও জুলুম স্বরূপ এ কাজ করবে, তাকে আমরা অবশ্যই জাহান্নামে পৌঁছে দেব।
এ আয়াতে ব্যবসাকে দুটো শর্তের ভিত্তিতে জায়েয ঘোষণা করা হয়েছেঃ
প্রথম, ব্যবসায় পক্ষদ্বয়ের পূর্ণ সন্তুষ্টি ও সম্মতির ভিত্তিতে সম্পন্ন হতে হবে এবং দ্বিতীয়, তাতে এক পক্ষের মুনাফা অপর পক্ষের ক্ষতির ফলে হতে পারবে না। আয়াতের তোমরা নিজেদের হত্যা করো না অংশ থেকে তাই প্রমাণিত হয়।
তাফসীরকারগণ উপরোদ্ধৃত আয়াতের যে দুটো তাফসীর পেশ করেছেন, এক্ষেত্রে এ দুটোই প্রযোজ্য। প্রথম তাত্পর্য, লোকেরা পরস্পরকে হত্যা করবে না। আর দ্বিতীয় হচ্ছে, তোমরা নিজেদের হাত নিজেদের হত্যা করবে না। উভয় দিক দিয়েই আয়াতটির সারকথা হচ্ছে, যে লোকই তার ব্যক্তিগত মুনাফা অর্জনের জন্যে অপরকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে, সে যেন সেই দ্বিতীয় ব্যক্তির রক্ত শুঁষে নিচ্ছে। আর তার পরিণতিতে নিজেই নিজের ধ্বংসের পথ উন্মুক্ত করে। অতএব চুরি, ঘুষখোরি, জুয়া ও ধোঁকা-প্রতারণা, খারাপ জিনিস দিয়ে ভাল জিনিসের মূল্য গ্রহণ ও সুদী কারবার- এ সব ধরনের কাজেই এ দুটো কারণ প্রকটভাবে বর্তমান। আর এ করণেই তা শরীয়তে সমর্থিত নয়। কোন কোন অবস্থায় পারস্পরিক সম্মতির শর্তটি পাওয়া গেলেও অপর গুরুত্বপূর্ণ শর্ত- তোমরা নিজেদের হত্যা কর না- (অর্থাৎ অপরের ক্ষতি না হওয়ার শর্ত) অনুপস্থিত। তাই তা জায়েয নয়।
[মওলানা মওদূদী লিখিত অর্থনীতির ভিত্তি]
তৃতীয় অধ্যায়
বিবাহ-শাদী ও পারিবারিক জীবনে হালাল-হারাম
স্বভাবগত কামনা চরিতার্থ করার ক্ষেত্রসীমা
বিবাহ
স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্ক
জন্মনিয়ন্ত্রণ
তালাক
পিতামাতা ও সন্তানদের পারস্পরিক সম্পর্ক
স্বাভাবিক কামনা চরিতার্থ করার ক্ষেত্রসীমা
আল্লাহ্ তা’আলা দুনিয়ায় মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এ উদ্দেশ্যে যে, মানুষ এখানে আল্লাহর খিলাফতের দায়িত্ব ও দুনিয়া আবাদকরণের কর্তব্য পালন করবে। এ কাজ সুসম্পন্ন হওয়ার জন্যে মানব প্রজাতির অস্তিত্ব রক্ষা পাওয়া এবং এখানে তাদের জীবনধারা অব্যাহতভাবে চলতে থাকা একান্তই আবশ্যক। তাহলেই মানুষ এখানে চাষাবাদের কাজ করতে পারে, শিল্প-প্রতিষ্ঠান কায়েম করে নিত্য পরিবর্তনশীল প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি উৎপাদন করতে পারবে। এক কথায় পৃথিবী আবাদকরণ, মানব সমাজের প্রতিষ্ঠা বিধান এবং আল্লাহর ন্যস্ত করা দায়িত্ব সমূহ পালন করে আল্লাহর হক্ক আদায় করা সম্ভবপর হতে পারে। এই উদ্দেশ্যের বাস্তবতা বিধানের জন্যেই আল্লাহ্ তা’আলা মানুষের স্বভাবে কতগুলো মৌলিক দাবি ও কামনা-বাসনা স্পৃহা-প্রবৃত্তি সুসংহত করে জন্মগতভাবেই রেখে দিয়েছেন। এই জিনিসই ব্যক্তি ও সমষ্টি গোটা মানব প্রজাতির স্থিতি ও অব্যাহত অগ্রগতির নিমিত্ত হয়ে আছে। মানুষকে এ কাজের জন্যে বাদ্য করে দেয়া হয়েছে।
তন্মধ্যে একটি হচ্ছে খাবার গ্রহণের ইচ্ছা। মানুষ পেট ভরে খাবার গ্রহণে উদ্যোগী হয় তার স্বাভাবিক ইচ্ছার কারণেই এবং এর ফলেই জীবনে বেচেঁ থাকা তার পক্ষে সম্ভবপর হয়।
দ্বিতীয় হচ্ছে, যৌন ইচ্ছা-কামনা-বাসনা। এরই ওপর মানব প্রজাতির রক্ষা পাওয়া- বংশের ধারা অব্যাহতভাবে নির্ভর করে। মানব প্রকৃতি নিহিত এই স্পৃহা অত্যন্ত তীব্র, শক্তিশালী ও নিয়ন্ত্রণ-অযোগ্য। তার বিশেষত্ব হচ্ছে, তা প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার নিজের ইচ্ছা-বাসনা হিসেবে চরিতার্থ করতে বাধ্য করতে একান্তভাবে বাধ্যঃ
যৌন স্পৃহা পর্যায়ে মানুষের ভূমিকা
১. মানুষ হয় এ স্পৃহার লাগাম খুলে দেবে। তা যদৃচ্ছ ও যত্রতত্র চরিতার্থ করার পথে কোন নিয়ন্ত্রণ বা সংযম রক্ষা করবে না। এ জন্যে কোন দ্বীনী, নৈতিক বা সামাজিক প্রতিবন্ধকতা বা নিয়ন্ত্রণকে একবিন্দু আমল দেবে না, সবকিছু লংঘন করে যাবে। এ ক্ষেত্রে একটি মত হচ্ছে, সবকিছু করা যাবে, কোন কিছুই নিষিদ্ধ নয়। এ মতের লোকেরা না কোন দ্বীন মানে, না কোন নৈতিক পবিত্রতায় তারা বিশ্বাসী। যৌন স্পৃহা চরিতার্থ করণে এ লোকেরা এই ভূমিকাই অবলম্বন করে। কিন্তু এ ভূমিকা মানুষকে পশু ও জন্তু-জানোয়ারের পর্যায়ে নিয়ে যায়। আর ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ তথা রাষ্ট্রে সর্বাত্মক বিপর্যয় ডেকে আনে।
২. দ্বিতীয় ভূমিকা এই হতে পারে যে, এ স্পৃহার মুকাবিলা করা হবে, তাকে প্রবল শক্তিতে দমন করা হবে, তাকে সমূলে ধ্বংস করা হবে, যেন এ ইচ্ছাটা কখনই মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে না পারে। কৃচ্ছ সাধনা, বৈরাগ্যবাদ ও সবকিছু থেকে নিজেকে বঞ্চিত রাখার প্রবণতা যাদের, এক্ষেত্রে তারাই উপরিউক্ত ভূমিকা অবলম্বন করে। এই ভূমিকায় এ স্বভাবগত প্রবণতাটাই খতম হয়ে যায়। এ স্পৃহা চরিতার্থ করার জন্যে জন্মগতভাবেই যে ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করা হয়েছে তা সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এ স্পৃহা মানব বংশ রক্ষায় যে অবদান রাখতে সক্ষম, উক্ত ভূমিকা তার সম্পূর্ণ পরিপন্থী।
৩. তৃতীয় ভূমিকা এই হতে পারে যে, এ স্পৃহা চরিতার্থ করার জন্যে একটা নিয়ম ও নিয়ন্ত্রণ কার্যকর করা হবে। তা এ নিয়ম ও নিয়ন্ত্রণের সীমার মধ্যে স্বাধীন ও উন্মুক্ত হবে, তাকে নির্মূলও করা হবে না, না পাগলের ন্যায় সীমালংঘনের কোন অনুমতি দেয়া হবে। আসমানী ধর্মসমূহ এই নীতিই করেছে। এ কারণে প্রায় সমস্ত ধর্মেই ব্যভিচার হারাম করা হয়েছে এবং বিবাহের সুষ্ঠু ব্যবস্থার প্রচলন করেছে। বিশেষত দ্বীন-ইসলাম মানুষের স্পৃহাকে স্বভাবগত শক্তিরূপে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং তা হালাল পথে চরিতার্থ করার জন্যে পন্থা উদ্ভাবন করেছে। অবিবাহিত ও নারী সংস্পর্শ পরিহার করে চলার প্রবণতাকে নিন্দা ও নিষেধ করেছে। অপর দিকে জ্বেনা-ব্যভিচার ও তার আনুসঙ্গিক যে যে কাজ মানুষকে সে দিকে টেনে নিয়ে যায়, তা সবই নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে।
বিবেচনা করে দেখলেই স্বীকার করতে হবে যে, ইসলাম অবলম্বিত নীতি ও ভূমিকাই মধ্যম ও সুবিচার ভারসাম্যপূর্ণ নীতি। কেননা বিবাহের ব্যবস্থা কার্যকর না হলে এ স্বভাবগত শক্তি মানব বংশের ধারা অব্যাহত রাখার ব্যাপারে তার দায়িত্ব পালন করতে অক্ষম থেকে যেত। পক্ষান্তরে জ্বেনা-ব্যভিচার হারাম করা না হলে নারীর জন্যে কোন পুরুষের সাথে বিবাহিত হয়ে নির্দিষ্ট হয়ে থাকার ব্যবস্থা দেয়া না হলে সেই পরিবার ব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারত না, যা প্রেম-প্রীতি প্রণয়-ভালবাসার লীলাকেন্দ্র হয়ে থাকে। এরূপ পরিবার সংস্থা গড়ে না উঠলে সমাজ গড়ে উঠতে পারে না। সমাজের উন্নতি অগ্রগতিরও কোন সুযোগ আসতে পারে না।
জ্বেনার কাছেও যাবে না
আমরা যখন দেখি, সমস্ত আসমানী দ্বীনই ঐক্যবদ্ধভাবে জ্বেনা-ব্যভিচারকে সম্পূর্ণরূপে হারাম করে দিয়েছে, তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষিত হয়েছে তখন আমাদের মনে এক বিন্দু বিস্ময়ের উদ্রেক হয় না। ইসলাম হচ্ছে আসমান থেকে অবতীর্ণ সর্বশেষ দ্বীন। এ ব্যাপারে তা খুব বেশি কঠোরতা অবলম্বন করেছে, নিষেধ করেছে, হারাম ঘোষণা করেছে এবং বংশ সংমিশ্রিত হওয়ার, বংশ বিনষ্ট হওয়ার, পারিবারিক ভাঙন ও বিপর্যয় সূচিত হওয়ার, পারস্পরিক শুভ সম্পর্ক বিনষ্ট হওয়ার, সংক্রামক ব্যধির প্রবাল্য সৃষ্টি হওয়ার, লালসার তীব্রতা বৃদ্ধির ও চরিত্র ধ্বংস হওয়ার সমস্ত কারণ সম্পর্কে বিশেষ সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছে। এ জন্যেই আল্লাহ্ তা’আলা শুধু জ্বেনা নিষেধ করেই ক্ষান্ত হন নি, তিনি বলেছেনঃ (আরবী****************)
তোমরা জ্বেনার কাছেও যাবে না। কেননা তা অতন্ত নির্লজ্জতার কাজ এবং খুবই খারাপ পথ। (সূরা বনী ইসরাঈলঃ ৩২)
আমরা দেখছি, ইসলাম যখন কোন কাজকে হারাম করে, তখন সেই হারাম কাজের সব ছিদ্রপথ- যে যে কাজ সেই পর্যন্ত মানুষকে পৌঁছে দেয় তা সবই বন্ধ করে হারাম ঘোষণা করে।
অতএব যেসব কাজ যৌন উত্তেজনা বৃদ্ধি করে, নারী বা পুরুষকে যা নৈতিক পতনের মুখে নিয়ে যায়, নির্লজ্জ কজে উদ্বুদ্ধ করে কিংবা তার কাছে পৌঁছে দেয়, সে কাজ সহজতর করে দেয়, ইসলাম সেসবই নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে, সম্পূর্ণ হারাম করে দিয়েছে। কেননা হারামের পথ উন্মুক্ত ও সহজসাধ্য হয়ে থাকলে সেই মূল হারাম থেকে রক্ষা পাওয়া কারো পক্ষেই সম্ভবপর হয় না। বিপর্যয় রোধ করা হয়ে যায় সম্পূর্ণ অসম্ভব।
ভিন মেয়েলোকের সাথে নিভৃতে সাক্ষাৎ হারাম
এ পর্যায়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে, ভিন্ মেয়েলোকের সাথে নিভৃত একাকীত্বে একত্রিত হওয়া এমতাবস্থায় যে, সে মেয়েলোকটি তার বিবাহিতা স্ত্রী নয়, মা-বোন-ফুফু-খালা প্রভৃতি মুহররমও নয়। এটা নিছক কোন অবিশ্বাসের ব্যাপার নয় বরং এরূপ অবস্থায় শয়তানী ওয়াসওয়াসায় পড়ে দুজনই চরিত্র হানিকর কাজে লিপ্ত হতে পারে। তা থেকে তাদের রক্ষা করার ব্যবস্থা এটা। মোমের সূতায় আগুন লাগালে তাপে মোম গলতে থাকাই স্বাভাবিক। দুই ভিন্ মেয়ে-পুরুষ যুবক-যুবতীর নিভৃত একাকীত্বে একত্রিত হতে পারাটাই উভয়কে পারস্পরিক আকর্ষণে একাকার করে দেয়ার অনিবার্য পরিস্থিতির উদ্ভব না হওয়াই বরং অস্বাভাবিক। কেননা তথায় তৃতীয় কেউ নেই। এ পর্যায়ে রাসূলে করীম (সা)-এর বাণী স্মরণীয়। ইরশাদ হয়েছেঃ (আরবী****************)
আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি যার ঈমান আছে সে যেন কোন নারীর সাথে এভাবে নিভৃত একাকীত্বে মিলিত না হয় যে, তথায় কোন মুহাররাম (পুরুষ বা মেয়েলোক) নেই। কেননা এরূপ সময়ে এ দুই জনের মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তি হিসেবে উপস্থিত থাকবে শয়তান। আর শয়তানের কারসাজি তো সকলেরই জানা আছে। (মুসনাদে আহমদ)
নবীর বেগমদের সম্পর্কে কুরআন মজীদের আয়াতঃ (আরবী****************)
তোমরা যদি নবীর বেগমগণের কাছে কোন জিনিস চাও তাহলে পর্দার আড়ালে থেকে চাইবে। তোমাদের ও তাদের অন্তর পবিত্র রাখার জন্যে এ এক উত্তম ব্যবস্থা। (সূরা আহযাবঃ ৫৩)
এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে ইমাম কুরতুবী লিখেছেনঃ
এ আয়াতে সে সব ভাবধারার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, যা মেয়েদের জন্যে পুরুষদের মনে ও পুরুষদের জন্যে মেয়েদের মনে স্বভাবতই জেগে ওঠে অর্থাৎ যদি পর্দার আড়ালে থেকে জিনিস চাওয়ার এ নীতি পালন করা হয়, তাহলে কোনরূপ সন্দেহের উদ্রেক হবে না। কেউ কোন মিথ্যা দোষারোপও করতে পারবে না। আর আত্মমর্যাদা রক্ষার জন্যেও এ ব্যবস্থা অধিক সতর্কতামূলক। এ থেকে একথাও বুঝতে পারা যায় যে, গায়র মুহাররম স্ত্রী লোকের সাথে নিভৃত একাকীত্বে মিলিত হলে নিজেকে বেঁধে না রাখতে পারার আশংকাই বেশি। তাই তা এড়িয়ে চলা উত্তম। এ পর্যায়ে নিজের নৈতিক পবিত্রতা রক্ষা করাও সহজ।
এ পর্যায়ে রাসূলে করীম (সা) স্বামীর নিকটাত্মীয়দের সাথে স্ত্রীর ঘনিষ্ট মেলামেশার ব্যাপারেও সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছেন। স্বামীর ভাই, চাচাতো ভাই ইত্যাদিই স্বামীর নিকটাত্মীয় এবং এদের সাথে ঘনিষ্ঠ মেলামেশা হওয়া অস্বাভাবিক নয়। এ ক্ষেত্রে প্রায়ই উপেক্ষা অবলম্বন করতে দেখা যায় এবং পরিণতি সম্পর্কে খুব কমই চিন্তা করা হয় অথচ আপন জনের সাথে ঘনিষ্ঠতা ও নিবিড় একাকীত্ব অধিকতর বিপজ্জনক। এরূপ অবস্থায় পদস্খলন হওয়াও অস্বাভাবিক বা বিরল নয়।
কেননা, ‘আপনজন’ যত সহজে স্ত্রীলোকের ঘরে প্রবেশ করতে পারে- প্রবেশ করলে কারো কিছু বলার থাকে না- সম্পূর্ণ অনাত্মীয় ও অপরিচিত জনের পক্ষে ততটা সহজ নয়।
স্ত্রীর নিজের অ-মুহাররম নিকটাত্মীয় পুরুষদের ক্ষেত্রেও এই কথা। তর চাচাতো ভাই, খালাতো-মামাতো ভাই এ পর্যায়ে গণ্য। কাজেই এদের মধ্যে কারো সাথে একাকীত্বে মিলিত হওয়া জায়েয নয়। নবী করীম (সা) ইরশাদ করেছেনঃ (আরবী****************)
তোমরা ভিন্ মেয়েলোকদের ঘনিষ্ঠ একাকীত্বে প্রবেশ করবে না। একজন আনসারী সাহাবী বললেনঃ হে রাসূল! আপনি স্বামীর নিকটাত্মীয়দের সম্পর্কে কি বলেন? রাসূলে করীম (সা) বললেনঃ স্বামীর নিকটাত্মীয়রা মৃত্যু সমতুল্য।
অর্থাৎ এই ঘনিষ্ট একাকীত্ব বিপদ ও ধ্বংস ডেকে আনে। গুনাহ যদি সঙ্ঘটিত হয়েই যায় তাহলে তো দ্বীনের দিক দিয়ে ধ্বংস হলো, আর স্বামী তা জানতে পেরে তাকে তালাক দিয়ে দিলে দাম্পত্য জীবনের বিপর্যয় শুরু হয়ে গেল। উপরন্তু নিকটাত্মীয়দের পরস্পরের প্রতি সন্দেহ, খারাপ ধারণা ও অনাস্থা এসে গেলে সামাজিক-সামস্টিক জীবনের সম্পর্ক-বন্ধন ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল। আর এ এক সর্বাত্মক বিপর্যয় সন্দেহ নেই।
সত্য কথা এই যে, ভিন্ পুরুষ নারীর নিভৃতে একাকীত্বে মিলিত হওয়ার প্রভাব শুধু মানুষে হৃদয়বেগ ও চিন্তা-ভাবনার ওপরই পড়ে না, গোটা পরিবার, স্বামী-স্ত্রী- দাম্পত্য জীবনের স্থিতি এবং তাদের পারস্পরিক গোপন কথাবার্তা ইত্যাদি সব কিছুর ওপরই তার তীব্র প্রতিক্রিয়া প্রতিফলিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী। উপরন্তু তা থেকে মিথ্যা দোষারোপকারী ও বকবককারী লোকদের পক্ষে ভিত্তিহীন কথা বলার একটা বিরাট সুযোগ জুটে যায়। এ ধরনের লোকদের লক্ষ্য দাম্পত্য জীবনের স্থিতি নিয়ে আসা নয়; ভাঙন বিপর্যয় সৃষ্টি করা মাত্র।
ইবনুর আমীর বলেছেন, আরবরা যেমন বলে (আরবী****************) (সিংহই মৃত্যু), বলে, (আরবী****************) (প্রশাসক আগুল), অর্থাৎ এ দুটো জিনিসের সাথে সাক্ষাৎ মানুষের জন্যে মৃত্যু ও আগুনের সাথে সাক্ষাতের সমান; তেমনি তারা বলে (আরবী****************) (স্বামীর নিকটাত্মীয় মৃত্যু তুল্য) অর্থাৎ স্বামীর নিকটাত্মীয়দের সাথে নিভৃত মিলিত হওয়া নিতান্ত অপরিচিত-অনাত্মীয় পুরুষের সাথে নিভৃত মিলিত হওয়ার তুলনায় অধিক মারাত্মক ও বিপজ্জনক। কেননা তারা অনেক সময় স্ত্রীর মনে এমন এমন জিনিসের চাহিদা সৃষ্টি করে দেয়, যা সংগ্রহ করে দেয় স্বামী-বেচারার পক্ষে বড়ই কঠিন ও দুষ্কর হয়ে থাকে। অনেক সময় তারা খারাপ আচরণ করতে উদ্ধত হয়ে থাকে। তা ছাড়া স্বামীর আত্মীয়-স্বজন তার অনুপস্থিতিতে তার ঘরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে তার গোপন অবস্থার তত্ত্ব জেনে যাবে, তা সে আদৌ পছন্দ করতে পারে না।
বিপরীত লিঙ্গের প্রতি লালসার দৃষ্টিতে তাকান
পুরুষ ভিন্ স্ত্রীলোকের ওপর দৃষ্টিপাত করবে কিংবা নারী ভিন্ পুরুষের প্রতি, ইসলাম এ ব্যাপারটিকে হারাম ঘোষণা করেছে। কেননা চক্ষু হৃদয়ের কুঞ্চিকা। দৃষ্টি বিপর্যয়ের আগাম সংবাদদাতা শক্তি, তা-ই জ্বেনার বার্তা বহনকারী। একজন প্রাচিন আরব কবি বলেছেনঃ (আরবী****************)
সর্বপ্রকার দুর্ঘটনার সূচনা দৃষ্টি থেকেই হয়। সামান্য ষ্ফুলিঙ্গ থেকেই সর্বগ্রাসী অগ্নিকুণ্ডলি জ্বলে উঠে।
এ কালের একজন কবি বলেছেনঃ (আরবী****************)
প্রথমে দৃষ্টি, পরে মিষ্টি স্মিত হাসি, তারপরে অভিবাদনের বিনিময়। তারপরে কথাবার্তা, তারপরে ওয়াদা প্রতিশ্রুতি আর শেষে সাক্ষাতকার।
এ করণে আল্লাহ্ তা’আলা সমস্ত মুমিন নারী-পুরুষকে পারস্পরিক চক্ষু নত রাখার নির্দেশ দিয়েছেন, সেই সাথে দিয়েছেন লজ্জাস্থানের পবিত্রতা সংরক্ষণ করার হুকুম। বলেছেনঃ (আরবী****************)
মুমিন পুরুষদের বল তাদের দৃষ্টি নত রাখতে ও তাদের লজ্জাস্থানের পবিত্রতা রক্ষা করতে। এ নীতিই তাদের জন্যে পবিত্রতার। তারা যা করে সে বিষয়ে আল্লাহ্ খুবই অবহিত। অনুরূপভাবে ঈমানদার মহিলাদের বল তাদের দৃষ্টি নত রাখতে ও তাদের লজ্জাস্থানের পবিত্রতা রক্ষা করতে।
এ দুটি আয়াতে নারী ও পুরুষ উভয়কেই নিজেদের দৃষ্টি নত রাখতে ও লজ্জাস্থানের পবিত্রতা রক্ষা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। দৃষ্টি নত রাখার জন্যে দেয়া নির্দেশের কুরআনে উদ্ধৃত ভাষা হচ্ছেঃ (আরবী****************) অর্থাৎ গোটা দৃষ্টি নত রাখার নয়, কোন কোন দৃষ্টি নত রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু লজ্জাস্থানের সংরক্ষণ পর্যায়ে কোন কোন অংশের কথা বলা হয়নি, সম্পূর্ণ ও সমগ্রভাবে সংরক্ষণের নির্দেশ দেয়া হয়েছ। কেননা শরীয়তের তাই কাম্য। কিন্তু দৃষ্টির ব্যাপারটি ভিন্নতর। প্রয়োজন পূরণ, বিপদ দূরীকরণ ও কল্যাণের পথ দেখার অপরিহার্যতার জন্যে আল্লাহ্ তাতে বিশেষ নম্রতা ও উদারতা দেখিয়েছেন। কিন্তু লজ্জাস্থানের ব্যাপারে এরূপ নয়।
অতএব কোন দৃষ্টি নত রাখার অর্থ এ নয় যে, মানুষকে চোখ বন্ধ করে নিতে হবে কিংবা মাথা মাটির দিকে এমনভাবে নুইয়ে নিতে হবে যে, মাটি ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। আয়াতের বক্তব্যও তা নয়। আর তা সম্ভবপরও নয়। সূরা লুকমানের ১৯ আয়াতে বলা হয়েছেঃ (আরবী****************) –এবং নিম্ন কর তোমার কোন কোন কণ্ঠধ্বনি।’ এ আয়াতে মুখ বন্ধ করে রাখতে বলা হয়নি, কণ্ঠের সব রকমের আওয়াজই যে ক্ষীণ হতে হবে এমন কথাও নয়। (আরবী****************) –এর অর্থ দৃষ্টিকে যথেচ্ছ বিচরণ করতে দেবে না, কাছাকাছি সব কিছুর ওপর দৃষ্টি পড়া বাঞ্ছনীয় নয়। কাজেই বিপরীত লিঙ্গের ওপর দৃষ্টি পড়লে- না দৃষ্টিকে নিবদ্ধ করে তার সৌন্দর্য-সুদা পান করায় লিপ্ত হবে, না ঘুরে ফিরে বারে বারে তাকে দেখবে। এ-ই হচ্ছে আয়াতের আসল বক্তব্য।
রাসূল করীম (সা) হযরত আলী (রা)-কে বলেছেনঃ (আরবী****************)
হে আলী, দৃষ্টির পর দৃষ্টি ফেলবে না। তুমি প্রথমবারই দেখতে পার, তারপর দ্বিতীয় বার নয়। (আহমদ, আবূ দাঊদ, তিরমিযী)
বিপরীত লিঙ্গের ওপর লোভী কামুক দৃষ্টিতে তাকানকে চোখের জ্বেনা বলেছেন। হাদীসের ভাষায় হচ্ছেঃ (আরবী****************)
চোখদ্বয়ও ব্যভিচার করে। আর তা হচ্ছে দৃষ্টিপাত। (বুখারী)
‘দৃষ্টিপাত’ কে জ্বেনা বলেছেন এজন্যে যে, তাতেও এক প্রকারের স্বাদ আস্বাদনের সুযোগ ঘটে। আর এ উপায়ে শরীয়ত-বিরোধী পন্থায় যৌন স্পৃহা চরিতার্থ করা হয়। ইনজীরে উদ্ধৃত হযরত ঈসার মুখ থেকেও অনুরূপ উক্তি রয়েছেঃ
আগে থেকে তোমাদের বলা হচ্ছিল যে, জ্বেনা করবে না, কিন্তু আমি বলছি, যে নিজ চোখ দিয়ে দেখল, সে জ্বেনা-ই করল।
এই লোভী লালসাপংকিল দৃষ্টি কেবল চারিত্রিক পবিত্রতা ও সতীত্বের জন্যেই বিপদজ্জনক নয়, মনের একনিষ্ঠতা ও হৃদয়ের শান্তি-স্বস্তির পক্ষেও তা খুবই ক্ষতিকর। কেননা তাতে মনে চরম অস্বস্তি ও অস্থিরতার সৃষ্টি হওয়া অবশ্যম্ভাবী।
লজ্জাস্থানের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ হারাম
ইসলামে দৃষ্টি নত রাখার নির্দেশ এক সাধারণ নির্দেশ। তাই লজ্জাস্থানের প্রতি দৃষ্টিপাত হলে সঙ্গে সঙ্গে চোখ ফিরিয়ে নেয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য। কেননা নবী করীম (সা) লজ্জাস্থানের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে নিষেধ করেছেন, তা কোন পুরুষের লজ্জাস্থান হোক কিংবা স্ত্রীলোকের, যৌন স্পৃহা সহকারে হোক কিংবা তা ছাড়াই এবং এ নির্দেশ নারী-পুরুষ উভয়ের জন্যে সমানভাবে প্রযোজ্য। নবী করীম (সা) বলেছেনঃ (আরবী****************)
কোন পুরুষ অপর পুরুষের লজ্জাস্থানের দিকে এবং কোন নারী অপর নারীর লজ্জাস্থানের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করবে না। এবং এক কাপড়ে কোন পুরুষ অপর পুরুষের সঙ্গে এক নারী অপর নারীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবে না।
পুরুষের লজ্জাস্থান বলতে বোঝায় নাভি থেকে হাটু পর্যন্তকার দেহাংশ। এ দিকে কোন পুরুষ বা মেয়েলোকের নজর দেয়া জায়েয নয়। অবশ্য ইবনে হাজম প্রমুখ কতিপয় ইমামের মতে উরু এর মধ্যে গণ্য নয়।
আর নারীর লজ্জাস্থান ভিন্ পুরুষের জন্যে মুখমণ্ডল ও দুই হাতের পাঞ্জাদ্বয় ব্যতীত সমগ্র দেহ। আর মুহাররম পুরুষের জন্যে- যেমন তার পিতা, ভাই- স্ত্রীলোকের লজ্জাস্থান সম্পর্কে আমরা পরে আলোচনা করব।
পরন্তু দেহের যে অংশ লজ্জাস্থান বলে চিহ্নিত, যার প্রতি অপর কারো দৃষ্টিপাত জায়েয নয়, তা হাত বা দেহাংশ দিয়ে স্পর্শ করাও অপরের জন্যে জায়েয নয়।
লজ্জাস্থান দেখা বা স্পর্শ করা সম্পর্কে এই যা কিছু বলা হলো তা সাধারণ অবস্থার কথা- যখন বাস্তবিকই কোন প্রয়োজন দেখা দেয় না। কিন্তু যদি সত্যিই কোন প্রয়োজন দেখা দেয়, তাহলে তখন তা হারাম হবে না; যেমন চিকিৎসা বা রিলিফ করা কালে এ প্রয়োজন দেখা দিয়ে থাকে। আর দৃষ্টিদান জায়েয বলে যা বলা হলো, তা এ শর্তে যে, এরূপ দৃষ্টিদানে কোনরূপ বিপদ ঘটার কারণ হবে না। অন্যথায় দৃষ্টিদানের অনুমতি নকচ হয়ে যাবে। কেননা মূল পাপের পথ বন্ধ করা শরীয়তের একটা প্রধান নিয়ম।
পুরুষ বা নারীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ
উপরে যা বলা হল তা থেকে এ কথাটা স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, পুরুষের লজ্জাস্থান বহির্ভূত- নাভি থেকে হাটু পর্যন্ত ছাড়া- দেহের অন্যান্য অংশের ওপর নারীর দৃষ্টি নিক্ষেপ জায়েয হবে ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ তাতে কোনরূপ যৌন স্পৃহা না জাগবে বা কোন ধরনের বিপদের আশংকা না থাকবে। রাসূলে করীম (সা) হযরত আয়েশা (রা)-কে হাবশীদের প্রতি তাকানোর অনুমতি দিয়েছিলেন, তারা তাদের অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে মসজিদে নববীতেই খেলা দেখাচ্ছিল। ফলে তিনি তাদের প্রতি পর্দার আড়াল থেকে তাকিয়ে দেখছিলেন। পরে তিনি নিজেই ক্লান্ত হয়ে পড়লে সেখান থেকে চলে গেলেন। (বুখারী, মুসলিম)
নারীর লজ্জাস্থান বহির্ভূত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ- মুখমণ্ডল ও দুই হাতের পাঞ্জার প্রতি পুরুষের তাকান জায়েয, যদি তাতে কোনরূপ যৌন লালসার সংমিশ্রণ না থাকে কিংবা পাপ সঙ্ঘটিত হওয়ার আশংকা না থাকে।
হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত হযরত আসমা বিনতে আবূ বকর (রা)- তাঁর বোন- নবী করীম (সা)-এর সম্মুখে হাযির হলেন। তার পরনে এমন পাতলা কাপড় ছিল যে, তা দিয়ে তাঁর দেহের কান্তি প্রস্ফূটিত হচ্ছিল। নবী করীম (সা) তা দেখে দৃষ্টি অন্যদিকে ফিরিয়ে নিলেন এবং বললেনঃ (আরবী****************)
হে আসমা, মেয়েলোক যখন পূর্ণ বয়স্ক হয়ে যায়, তখন তার মুখমণ্ডল ও হাতের পাঞ্জাদ্বয় ব্যতীত দেহের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কোন কিছুই দৃশ্যমান হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। (আবূ দাঊদ)
হাদীসটি যদিও সূত্রের বিচারে দুর্বল, কিন্তু এ পর্যয়ে বহু কয়টি সহীহ হাদীসে বিহদের আশংকা না থাকলে মুখমণ্ডল ও হাতের পাঞ্জাদ্বয়ের ওপর দৃষ্টিপাত জায়েয হওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে বলে উক্ত হাদীসটির সে দুর্বলতা দূর হয়ে গেছে।
সারকথা হচ্ছে, পুরুষ বা নারীর লজ্জাস্থান বহির্ভূত অঙ্গের প্রতি নির্দোষ দৃষ্টিপাত জায়েয এবং হালাল। তবে বারবার তাকানো এবং সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে স্বাদ নিয়ে তাকানো জায়েয নয়। কেননা তাতেই বিপদ সঙ্ঘটিত হওয়ার আশংকা রয়েছে।
তবে যে অঙ্গ দেখা হালাল নয় তার দিকে আকস্মিকভাবে দৃষ্টি পড়ে যাওয়ায় কোন দোষ ধরা হবে না। এটা ইসলামের উদারতা। হযরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেনঃ (আরবী****************)
রাসূলে করীম (সা)-কে আকস্মিক দৃষ্টি পড়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেনঃ তোমার দৃষ্টি অন্যদিকে ফিরিয়ে নাও।
অর্থাৎ সে একবারের পর দ্বিতীয়বার তাকাবে না।
নারীর সৌন্দর্য প্রকাশ সমস্যা
উপরে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়া সম্পর্কে কথা বলা হয়েছে। দুটো আয়াতে এ পর্যায়ে নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্যে বিধান দেয়া হয়েছে। এর তৃতীয় আয়াতটিতে নারীদের জন্যে বিশেষভাবে একটি নের্দেশের উল্লেখ হয়েছে। নির্দেশটি এইঃ (আরবী****************)
তারা তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ করবে না। তবে যা স্বতঃই প্রকাশ হয়ে পড়ে তার কথা স্বতন্ত্র। (সূরা নূরঃ ৩১)
নারীর ‘সৌন্দর্য’ বলতে সেসব জিনিসই বোঝায়, যা তাকে সৌন্দর্যমণ্ডিতা ও রূপসী বানিয়ে দেয়। এর মধ্যে মুখমণ্ডল, কেশদাম ও দৈহিক লালিমা প্রভৃতি জন্মগত সৌন্দর্য শামিল রয়েছে। যেমন রয়েছে কাপড়, অলংকার ও প্রসাধনী দ্রব্যাদি প্রভৃতি দ্বারা অর্জিত সৌন্দর্য ও রূপ-মাধুর্য। আল্লাহ্ তা’আলা পূর্বোদ্ধৃত আয়াতটিতে নারীদের নির্দেশ দিয়েছেন তাদের সৌন্দর্য লুকিয়ে রাখতে, প্রকাশ হতে না দিতে। তা থেকে বাইরে থাকছে শুধু তা যা স্বতঃই প্রকাশ হয়ে পড়ে।
এই স্বতঃই প্রকাশ হয়ে পড়ে বলতে কি বোঝায়, তা নির্ধারণে বিভিন্ন তাফসীরকার বিভিন্ন সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন।
প্রশ্ন তোলা হয়েছে, ‘স্বতঃই প্রকাশ হয়ে পড়ে’ বলতে প্রয়োজনের কারণে কোনরূপ ইচ্ছা ছাড়াই যা প্রকাশ হয়ে পড়ে তা-ই কি বোঝায়? যেমন বাতাসের ঝাপটায় কোন কিছু প্রকাশ হয়ে পড়ল? অথবা তার অর্থ হবে, সাধারণত ও অভ্যাসবশত যা প্রকাশিত হয়? .....এ ব্যাপারে আসল কথা হচ্ছে প্রকাশিত হওয়া।
পূর্বকালের মনীষীদের মধ্যে অধিকাংশ লোক এ শেষোক্ত মতই পোষণ করতেন বলে বর্ণিত হয়েছে।
হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি ‘যা স্বতঃই প্রকাশ হয়ে পড়ে’ অংশের তাফসীরে বলেছেন, তা হচ্ছে চোখের সুরমা, কাজল, পাউডার, অঙ্গুরীয় প্রভৃতি। হযরত আনাস (রা) থেকেও অনুরূপ মত বর্ণিত হয়েছে।
চোখে সুরমা লাগান ও আঙ্গুলে আঙ্গুরীয় পরিধান করা মুবাহ্। সেজন্যে এ দুটো স্থানের প্রকাশ পাওয়া অনিবার্য। আর তা হচ্ছে মুখমণ্ডল ও পাঞ্জাদ্বয়। হযরত সায়ীদ ইবনে জুবাইর, আতা, আওযায়ী প্রমুখ থেকেও এরূপ মতই বর্ণিত হয়েছে।
হযরত আয়েশা ও কাতাদাহ প্রমুখ দুহাতের কংকনকেও এর মধ্যে শামিল করেছেন। যে সৌন্দর্য প্রকাশ করা নিষিদ্ধ, বাহুর সে অংশ তা থেকে বাদ পড়ে যায়। মুষ্টি থেকে অর্ধেক বাহু পর্যন্ত সীমা নির্ধারণে মতের বিভিন্নতা বিদ্যমান।
এ প্রশস্ততার বিপরীত অন্যরা সংকীর্ণতার অবতারণা করেছেন। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসঊদ ও নখয়ী প্রমুখ ‘যা স্বতঃই প্রকাশিত হয়ে পড়ে’ কথাটির ব্যাখ্যায় বলেছেন, তা হচ্ছে চাদর ও কাপড়, যা দেহের বাইরে পরা হয়। কেননা তা গোপন করা ও ঢেকে রাখা সম্ভব নয়।
তবে সাহাবী ও তাবেয়ীনের অনেকে ‘যা স্বতঃই প্রকাশিত হয়ে পড়ে’ কথাটির ভিত্তিতে স্পষ্ট করে বলেছেন যে, তা হচ্ছে মুখমণ্ডল ও দুই পাঞ্জা এবং এ ছাড়া যে সৌন্দর্য থাকবে না, তা। আর আমি এ সবকেই অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য বলে মনে করি। হাতের আঙ্গুরীয় ও চোখের সুরমা ইত্যাদি এর মধ্যে গণ্য।
সিঁদুর, পালিশ, পাউডারের ব্যাপারটি এ থেকে ভিন্নতর। একালের মেয়েরা এসব কপোল, ওষ্ঠাধর ও নখে ব্যবহার করে। কিন্তু তা খুব অবাঞ্ছনীয় বাড়াবাড়ি। এসব শুধু ঘরের মধ্যেই ব্যবহার করা যেতে পারে। কিন্তু অধুনা মেয়েরা ঘরের বাইরে যাওয়ার সময় পুরুষদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে এসব ব্যবহার করে থাকে। কিন্তু এ কাজটি সম্পূর্ণ হারাম। ‘যা স্বতঃই প্রকাশিত হয়’-এর অর্থে শুধু চাদর বা বোরকা প্রভৃতি বাহ্যিক জিনিসগুলোই বোঝান হয়েছে’ মনে করা সমীচীন নয়। কেননা এসব কাপড়ের প্রকাশিত হওয়া তো একটা অতি স্বাভাবিক ব্যাপার, প্রকাশ না হয়েই পারে না। তাই তা গোপন করার কোন আদেশ হতেই পারে না। আর শুধু ‘বাতাসের ধাক্কায় যা প্রকাশিত হয়ে পড়ে’ মনে করাও গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা এতে মানুষের কোন দখল নেই। কাজেই সে বিষয়ে কিছু বলা-না-বলা সমান। ঐ কথাটি দ্বারা যা সহজেই বুঝতে পারা যায়, তা হচ্ছে, যা লুকানো যায়, প্রকাশ করার ব্যাপারে এগুলো বাদ যাবে। ঈমানদার মহিলাদের জন্যে এটা একটা সুবিধা দান পর্যায়ের কথা। আর এ সুবিধাদান যে মুখমণ্ডল ও কবজিদ্বয় সম্পর্কেই থাকা উচিত, তা অবশ্যই যুক্তিসঙ্গত কথা।
মুখমণ্ডল ও পাঞ্জাদ্বয় সম্পর্কে এ সুবিধাদানের যৌক্তিকতা অনুধাবন করতে হবে। কেননা এ দুটো সব সময় লুকিয়ে রাখা মেয়েদের জন্যে খুবই কষ্টকর। বিশেষ করে বৈধ প্রয়োজনে ঘরের বাইরে যেতে হলে তখন যে এ দুটো অংশ প্রকাশ করা জরুরী হয়ে পড়ে তা অস্বীকার করা যায় না। যেমন বিধাবা মেয়েলোকের পক্ষে তার ইয়াতীম সন্তানদের জন্যে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করা এবং দরিদ্র পরিবারের মেয়েদের তাদের স্বামীদের সাহায্যার্থে বাইরে বের হতে হলে মুখমণ্ডল ও কবজি উন্মুক্ত করা তো অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এরূপ অবস্থায় মুখমণ্ডল ও কবজিদ্বয় আবৃত করা হলে চলাফেরা করা বড়ই কঠিন ও কষ্ঠকর হয়ে পড়বে।
ইমাম কুরতুবী বলেছেনঃ
চেহারা ও কবজিদ্বয় সাধারণতঃ বিশেষ করে নামায, হজ্জ, উমরা প্রভৃতি ইবাদত করার সময়- খুলেই যায়। তাই ‘তবে স্বতঃই যা প্রকাশিত হয়ে পড়ে’ বলে এসব অঙ্গ আবৃত রাখার নির্দেশের বাইরে রাখা হয়েছে বলে মনে করাই অধিকতর যথার্থ কথা। হযরত আয়েশা (রা) বর্ণিত হাদীস এ কথাই বলে। হাদীসটি এই (পূর্বেও উদ্ধৃত হয়েছে) : (আরবী****************)
হযরত আবূ বকর (রা)-এর কন্যা আসমা নবী করীম (সা)-এর সমীপে উপস্থিত হলে- তার পরনে ছিল পাতলা কাপড়। রাসূলে করীম (সা) তাঁর দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলেন এবং বললেনঃ হে আসমা! মেয়েলোক পূর্ণ বয়স্কা হয়ে গেলে তার দেহের মুখমণ্ডল ও কবজিদ্বয় ছাড়া আর কিছুই দৃশমান হওয়া উচিত নয়।
আল্লাহ্ তা’আলার নিম্নোক্ত কথাটি থেকেও উপরিউক্ত কথারই সমর্থন মেলেঃ (আরবী****************)
মুমিনদের বলুন, তারা যেন তাদের চোখ নিম্নমুখী রাখে। (সূরা নূরঃ ৩০)
এ থেকেই বোঝা যায় যে, মেয়েদের মুখমণ্ডল আবৃত নয়- উন্মুক্ত- বলেই পুরুষদের বলা হয়েছে চোখ নিম্নমুখী রাখতে অর্থাৎ সে মুখের দিকে তাকাবে না।
কেননা সমস্ত দেহসহ মুখমণ্ডলও যদি আবৃত থাকে তাহলে চোখ নীচু রাখতে বলার কোন অর্থ হয় না। কেননা ওখানে দেখবার মতো তো কিছুই নেই।
এতদসত্ত্বেও মুসলিম নারী তার যাবতীয় সৌন্দর্য-অলংকার লুকিয়ে রাখার জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা করা কর্তব্য। এমনকি মুখমণ্ডলও উন্মুক্ত করা উচিত নয়। কেননা মুখমণ্ডল দেখেই তা নৈতিক বিপর্যয়ের সূচনা হয়। এ যুগে খোদাদ্রোহিতার ব্যাপক প্রচলন এ প্রয়োজনকে আরও তীব্র করে দিয়েছে। নারী-সুন্দরী রূপসী হলে তো মুখমণ্ডলকে ঢেকে রাখা ছাড়া অন্য কোন কথা চিন্তাই করা যায় না। কেননা নারী মুখের রূপ-সৌন্দর্যই পুরুষকে আকৃষ্ট করে সবচাইতে বেশি।
(আরবী****************)
এবং নিজেদের বক্ষদেশের ওপর নিজেদের দোপাট্রার আচঁল চেপে রাখেবে।
মুসলিম নারীকে তার দোপাট্টা দ্বারা তার মাথা ঢেকে রাখতে হবে, মাথার উপর আবরণ চাপিয়ে রাখবে, যে-কোন ধরনের কাপড় দ্বারা সম্ভব হোক তার বক্ষকে অবশ্যই আবৃত করে রাখবে। যেন এসব বিপদ সৃষ্টিকারী অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অনাবৃত হয়ে ন যায় এবং দুষ্ট লোকদের সন্ধানী দৃষ্টি ও মৌমাছিদের লোলুপ চোখ সে সবের ওপর পড়তে না পারে।
(আরবী****************)
এবং তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ করবে না তাদের স্বামী ও পিতাদের ছাড়া অন্য কারো সামনে। (সূরা নূরঃ ৩১)
এ আদেশ মুমিন নারীদের গোপন সৌন্দর্য ভিন্ পুরুষেদের সম্মুখে প্রকাশ না করতে বরং লুকিয়ে রাখতে বলা হয়েছে। এ গোপন সৌন্দর্য বলতে কান, চুল, গ্রীবা, ঘাড়, বুক, পায়ের নালা ইত্যাদি বোঝায়। ভিন্ পুরুষদের সম্মুখে মুখমণ্ডল ও পাঞ্জাদ্বয় প্রকাশ করার অনুমতি দেয়া সত্ত্বেও এ নিষেধ বাণী উচ্চারিত হওয়া খুবই গুরুত্ববহ।
বারো শ্রেণীর মানুষকে এ নিষেধবাণীর বাইরে রাখা হয়েছেঃ
১. তাদের স্বামী। অতএব স্বামীর পক্ষে স্ত্রী দেহের যে কোন অঙ্গ দেখা সম্পূর্ণ জায়েয। হাদীসে বলা হয়েছেঃ (আরবী****************)
তোমার লজ্জাস্থান তোমান স্বামী ছাড়া আর সকলের থেকে রক্ষা কর- আবৃত রাখ।
২. পিতা, দাদা, পরদাদা এর মধ্যে শামিল, তা বাবার দিক থেকে হোক কিংবা মার দিকে থেকে।
৩. স্বামীর পিতা, তার নিজের পিতার সমান।
৪. তাদের পুত্র, তাদের সন্তানের পুত্ররা- মেয়েরাও এর অন্তর্ভুক্ত।
৫. স্বামীর পুত্র- এ এক অনিবার্য ব্যাপার। তাছাড়া সে ঘরে এদের জন্যে মা স্বরূপই বটে।
৬. তাদের ভাই আপন ও সৎ-এক মা বা এক পিতার সন্তান হিসেবে।
৭. ভাইয়ের পুত্র, কেননা ফুফু-ভাতিজার মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক সম্পূর্ণ হারাম।
৮. বোন-পুত্র কেননা খালা-বোন পুত্রের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক চিরতরে হারাম।
৯. তাদের নারীকুল। আপন আত্মীয়া নারী-বংশের দিক দিয়ে আপন কিংবা দ্বীনের দিক দিয়ে, সকলের সাথে অবাধ সাক্ষাৎ চলতে পারে। তবে অমুসলিম নারীদের মুসলিম নারীর সৌন্দর্য দেখান জায়েয নয়। শুধু ততটুকুই দেখান যেতে পারে, যতটা ভিন্ পুরুষকে দেখান যায়।
১০. ক্রীতদাস-দাসী। কেননা ইসলাম তাদের পরিবারের অঙ্গ বানিয়ে দিয়েছে। কোন কোন ইমামের মতে এ অনুমতি কেবল দাসীদের বেলায়, দাসদের বেলায় নয়।
১১. অধীন ও প্রয়োজনহীন পুরুষ। এরা একে তো অধীন, দ্বিতীয়তঃ এদের নারীর প্রতি কোন বিশেষ আকর্ষণ নেই- হয় শারীরিক অক্ষমতার কারণে কিংবা বুদ্ধি-বিবেকের দিক দিয়ে অপরিপক্ক হওয়ার কারণে। সাধারণ বেতনভুক কর্মচারী যারা বাড়ির কাজকর্ম করে ও ঘরে আসা যাওয়া করতে বাধ্য হয়, অথচ যৌন আকর্ষণ না থাকার দরুন কোনরূপ বিপদের আশংকাও নেই।
১২. যেসব বালক এখনও নারীর লজ্জাস্থানের প্রতি কোন আকর্ষণ লাভ করে নি। ওরা বয়সে ছোট, নাবালেগ, যৌন চেতনা জাগানি এখনও। সে চেতনা জেগেছে বলে টের পেলে নারীর গোপন সৌন্দর্য তাদের সম্মুখে উন্মক্ত করা জায়েয নয়। পূর্ণ বয়স্ক না হলেও নয়।
কুরআনের আয়াতে চাচা ও মামার উল্লেখ করা হয়নি। কেননা তারা পিতার সমতুল্য। হাদীসে বলা হয়েছেঃ (আরবী****************)
চাচা পিতার সমতুল্য
নারীদের সতর
পূর্বকর্তী আলোচনা থেকে আমরা জানতে পেরেছি, নারীদেহের যে যে অংশ প্রকাশ করা জায়েয নয়, তা-ই তার লজ্জাস্থান এবং তা ঢেকে রাখা ওয়াজিব, তা উন্মুক্ত রাখা সম্পূর্ণ হারাম।
অতএব ভিন্ পুরুষদের সম্মুখে এবং অমুসলিম নারীদের ক্ষেত্রেও- নারীর মুখমণ্ডল ও কবজিদ্বয় ব্যতীত সমস্ত দেহই লজ্জাস্থান- অবশ্যই আবৃত রাখতে হবে। মুখমণ্ডল ও কবজিদ্বয় যেহেতু কাজকর্ম গ্রহণ-দান ইত্যাদি কাজের জন্যে উন্মুক্ত রাখা অপরিহার্য এ কারণে তা অনাবৃত রাখা জায়েয যেনম ইমাম রাযী লিখেছেন। এ ছাড়া দেহের যে অঙ্গ উন্মুক্ত রাখা বা করা জরুরী নয়, তা ঢেকে রাখার জন্যে আদেশ করা হয়েছে। স্বভাবগতভাবে যা উন্মুক্ত রাখা হয় এবং যা প্রকাশ করার প্রয়োজন দেখা দেয় তা খুলে রাখার অনুমতি দেয় হয়েছে। কেননা ইসলামী শরীয়তের বিধান ভারসাম্যপূর্ণ, মানব কল্যাণমুখী। ইমাম রাযী লিখেছেনঃ
মুখমণ্ডল ও পাঞ্জাদ্বয় প্রকাশ করা অপরিহার্য বলে তা নারীদের গোপন অঙ্গের মধ্যে গণ্য নয় বলে সকলেই ঐকমত্য প্রকাশ করেছেন। তবে পা উন্মুক্ত রাখা অপরিহার্য নয়। তাই তা নারীর গোপন অঙ্গের মধ্যে গণ্য কিনা- এ নিয়ে মতভেদের সৃষ্টি হয়েছে। (আরবী****************)
সূরা নূর-এর আয়াতে যেমন বলা হয়েছে, উপরিউক্ত বারো শ্রেণীর পুরুষদের ক্ষেত্রে কান, ঘাড়, চুল, বুক, বাহুদ্বয় ও নলাদ্বয় ব্যতীত সমস্ত অঙ্গ আবৃত করে রাখতে হবে। তাদের সম্মুখে এ সব অঙ্গ প্রকাশ করার অনুমতি দেয়া হয়েছে শরীয়তে। এ ছাড়া দেহের অন্যান্য অঙ্গ ও অংশ যেমন পিঠ, পেট, লিঙ্গস্থান, উরুদ্বয় প্রভৃতি স্বামী ছাড়া অপর কোন পুরুষ বা নারীর সম্মুখে উন্মুক্ত করা একেবারেই জায়েয নয়।
আয়াতের এ তাৎপর্য কয়েকজন ইমামের মতের খুবই নিকটবর্তী। মুহাররম পুরুষদের জন্যে নারীর লজ্জাস্থান শুধু নাভি ও হাটুর মধ্যবর্তী অংশ। অন্য নারীদের জন্যেও এই পর্যন্তই সীমা। কোন কোন বিশেষজ্ঞের মতে নারীর লজ্জাস্থান মুহাররম পুরুষের জন্যে শুধু এতটুকু যতটা কাম-কাজ করার সময়ও উন্মুক্ত হয় না। ঘরে কাজ-কাম করার সময় নারীদেহের যেসব অংশ সাধারণত উন্মুক্ত থাকে, মুহাররম পুরুষদের সেদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করাও নাজায়েয নয়।
মু’মিন নারীদের প্রতি আল্লাহর নির্দেম হচ্ছে, তারা যখন ঘরের কাজে বইরে যাবে তখন একটি বড় চাদর দ্বারা সমস্ত দেহ আবৃত করে নেবে। এর ফলে অন্যান্য কাফির ও খারপ চরিত্রের নারীদের থেকে তাদের স্বাতন্ত্র্য সকলেরই সম্মুখে প্রতিভাত হবে। আল্লাহ্ তা’আলা তাঁর নবীকে উম্মতের সকলকে একথা জানিয়ে দেয়ার জন্যে নির্দেশ দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছেঃ (আরবী****************)
হে নবী! আপনি আপনার স্ত্রীদের, কন্যাদের ও মুমিন নারীদের বলে দিন যে, তারা যেন তাদের দেহের ওপর চাদর ফেলে রাখে। এ এক উত্তম পন্থা। এর ফলে তাদের চেনা যাবে এবং তাদের কেউ জ্বালাতন করবে না।
(আরবী****************) বহু বচনের শব্দ। এক বচনে (আরবী****************) তার অর্থ প্রশস্ত কাপড়। এ কালের বোরকা এ পর্যায়ে পড়ে।
জাহিলিয়াতের যুগে নারীরা যখন ঘর থেকে বাইরে যেত, তখন নিজেদের কোন কোন সৌন্দর্য- বুক, ঘাড়-গলা, চুল প্রভৃতি খোলা রাখত। দুষ্ট চরিত্রের লোকেরা তাদের পিছে লেগে যেত। এ অবস্থায় এ আয়াত নাযিল হয়েছে। এতে মুমিন নারীদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তারা তাদের চাদরের একাংশ মাথায় দিয়ে রাখে যেন দেহের এসব অংশ আবৃত হয়ে থাকে। আর বাহ্যিক চিত্র দেখে যেন তাদের পবিত্র চরিত্রের নারী বলে চেনা যায়। ফলে কোন মুনাফিক ও নির্লজ্জ পুরুষ তাদের উত্যক্ত করবে না, করার সাহস পাবে না।
আয়াতে একটি কারণ স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করেছে। আর তা হচ্ছে, চরিত্রহীন ও দুষ্ট লোকদের দ্বারা স্ত্রী লোকদের জ্বালাতন করা, উত্যক্ত করা, তাদের প্রতি তাকান মেয়েদের মধ্যে ভয়ের কারণ নিহিত নেই এবং তাদের প্রতি কোন অবিশ্বাসও আরোপ করা হয়নি। যদি কেউ তা মনে করেন তবে তার কোন যুক্তি নেই। কেননা উলঙ্গ সুসজ্জিতা নারী কিংবা লাস্যময়ী ও লীলায়িত ভঙ্গিমায় বিচরণশীলা নারী চিরকাল পুরুষের মনে যৌন উত্তেজনা ও লালসা-কামনার সৃষ্টি করে থাকে। মেয়েদের সাথে যারা হাতাহাতি বা হাত ধরাধরি করে, তারাই লোভাভুর ও কামনা কাতর হয়ে পড়ে।কুরআনে তাই বলা হয়েছেঃ (আরবী****************)
নম্র কণ্ঠস্বরে কথা বলবে না, তাহলে হৃদয়ের রোগী পুরুষ কামাতুর হয়ে হড়বে।
মুসলিম মহিলার পর্দা ও সতীত্ব রক্ষার ব্যাপারে ইসলাম বিশেষ কঠোরতা অবলম্বন করেছে। এ ব্যাপারে খুব সামান্যই উদারতা দেখান হয়েছে। যেমন বৃদ্ধ মহিলার পর্দার ব্যাপারে কিছুটা নম্রতা প্রদান প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা’আলা ইরশাদ করেছেনঃ (আরবী****************)
বৃদ্ধা মহিলা- যারা বিয়ের আশা পোষণ করে না- তারা নিজেদের গায়ের চাদর যদি খুলে রেখে দেয়, তাহলে তদের কোন গুনাহ হবে না। তবে শর্ত এই যে, তারা সৌন্দর্য ও অলংকার প্রদর্শনকারিণী হতে পারবে না। কিন্তু তারা যদি এ ব্যাপারে সতর্কতাবলম্বন করে, তাহলে তাদের পক্ষে খুবই কল্যাণকর। আর আল্লাহ্ সব কিছুই শোনেন, সব কিছুই জানেন।
আয়াতে (আরবী****************) বলতে সেসব মহিলাকে বুঝিয়েছে, যারা বার্ধক্যজনিত কারণে অবসরপ্রাপ্ত হয়েছে, যাদের হায়েয হয় না, সন্তান হওয়ারও যাদের কোন আশা নেই। এ কারণে তারা পুনরায় বিবাহিতা হওয়ার জন্যে আকাঙ্খিত নয়। পুরুষদের প্রতিও নেই তাদের কামনা-বাসনা-আগ্রহ। পুরুষরাও তাদের প্রতি কোন আকর্ষণ বোধ করে না, এরূপ নারীর পর্দা ও লজ্জাস্থান আবৃত রাখার ব্যাপারে নিয়মকে হালকা করে দিয়েছেন। তিনি তাদের অনুমতি দিয়েছেন, এরা তাদের বাহ্যিক ও প্রকাশমান কাপড়- চাদর বা বোরকা ইত্যাদি খুলে ফেলতে পারে।
এ সুযোগটুকুও দেয়া হয়েছে শর্তাধীনে। সে শর্ত হচ্ছে, তারা লোকদের দেখানর উদ্দেশ্যে কাপড় খুলে ফেলতে পারবে না। প্রয়োজনে সুবিধা যে, এ সুযোগটা কাজে লাগাতে পারবে।
এ সুযোগ সত্ত্বেও উত্তম নীতি গ্রহণ করা সর্বপ্রকার শোবাহ-সন্দেহ থেকে মুক্ত থাকার জন্যে সতর্কতা অবলম্বন করাই তাদের জন্যে ভল।
সাধারণ গোসলখানায় নারীর প্রবেশ
নারীর পর্দা ও ইজ্জত রক্ষার উদ্ধেশ্যে ইসলাম যে কড়াকড়ি নীতি গ্রহণ করেছে, তাতে রাসূলে করীম (সা) সাধারণ গোসল খানায় নারীদের প্রবেশ করা ও অন্যান্য নারীদের সামনে পরিধানের কাপড় খুলে ফেলার ব্যাপারে খুবই কড়া নিষেধবাণী উচ্চারণ করেছেন। কেননা এসব সাধারণ নারী অন্যান্য মেয়েদের দৈহিক গুণাবলী তাদের সাধারণ সভা-মজলিসে বর্ণনা করে খুবই স্বাদ গ্রহণ করতে অভ্যস্ত।
নবী করীম (সা) পুরুষদেরও কোন লুঙ্গী-গামছা না পরে, সাধারণ গোসলখানায় প্রবেশ করতে নিষেধ করেছেন। কেননা অন্যদের সামনে উলঙ্গ হওয়াটা ইসলামে আদৌ পছন্দনীয় কাজ নয়। হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, হযরত নবী করীম (সা) বলেছেনঃ (আরবী****************)
যে লোক আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি ঈমানদার, সে যেন সাধারণ গোসল খানায় লুঙ্গী ছাড়া প্রবেশ না করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি ঈমানদার, সে যেন তার স্ত্রীকে সাধারণ গোসলখানায় প্রবেশ করতে না দেয়।
হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিতঃ (আরবী****************)
রাসূলে করীম (সা) গোসলখানায় প্রবেশ করতে প্রথমে সাধারণভাবেই নিষেধ করে দিয়েছিলেন। পরে পুরুষদের জন্য লুঙ্গীসহ প্রবেশ করার অনুমতি দিয়েছেন।
মেয়েদের জন্যে সুবিধা দান করা হয়েছে এক্ষেত্রে যে, তাদের কোন রোগের চিকিৎসা কিংবা নেফাস ইত্যাদি নিরাময়তার জন্যে গোসলখানায় প্রবেশ করতে পারে।
হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিতঃ (আরবী****************)
নবী করীম (সা) সাধারণ গোসলখানাসমূহ পর্যয়ে বলেছেন, তাতে পুরুষরা যেন লুঙ্গী না নিয়ে প্রবেশ না করে। আর মেয়েদের তোমরা তাতে প্রবেশ করা থেকে নিষেধ কর। তবে রোগীনী কিংবা নেফাসের স্ত্রীলোক প্রবেশ করতে পারে। (ইবনে মাযাহ, আবূ দাঊদ)
এ হাদীসের সনদে কিছুটা দুর্বলতা রয়েছে। কিন্তু শরীয়তের সাধারণ বিধানে রোগীদের জন্যে যেমন অনেক সুযোগ-সুবিধা দেয়া হয়েছে, অনেক ইবাদত ও ওয়াজিব কাজ করা থেকে রেহাই দান করা হয়েছে, সে দৃষ্টিতে এ হাদীসের প্রতিপাদ্য অনেকটা শক্তিশালী হয়ে উঠে। যেমন ইসলামী আইনের প্রসিদ্ধ মূলনীতি স্বরূপ বলা হয়েছেঃ (আরবী****************)
কোন হারাম কাজ বন্ধ করার জন্যে তার কারণ বা পথও হারাম ঘোষিত হয়ে থাকলে প্রয়োজন ও সাধারণ জনকল্যাণের প্রশ্নে তা মুবাহ হয়ে যায়।
এ দিক দিয়েও উপরিউক্ত কথার সত্যতা জানা যায়।
হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণিত হাদীসও এ কথারই সমর্থন দেয়। হাদীসটি এইঃ (আরবী****************)
নবী করীম (সা) বলেছেনঃ তোমরা ‘হাম্মাম’ নামক ঘর থেকে দূরে সরে থাকবে। সাহাবিগণ বললেনঃ ইয়া রাসূল! হাম্মাম তো ময়লা দূর করে ও রোগীকে উপকার দেয়? তখন তিনি বললেনঃ তাহলে যে-ই তাতে প্রবেশ করবে সে যেন স্বীয় লজ্জাস্থান আবৃত রাখে। (হাকেম)
এমতাবস্থায় কোন নারী যদি কোনরূপ ওযর বা প্রয়োজন ব্যতীতই তাতে প্রবেশ করে, তাহলে সে একটা হারাম কাজ করল এবং এজন্যে রাসূলে করীম (সা) যে কঠোর বাণী উচ্চারণ করেছেন, সে তার যোগ্য হলো। আবূর মুলাইছ আল-হাযালী (রা) বর্ণনা করেছেনঃ (আরবী****************)
হিমস কিংবা সিরিয়ার কিছু সংখ্যক মেয়েলোক হযরত আয়েশা (রা)-এর কাছে উপস্থিত হলো। তিনি বললেনঃ তোমরা কি সাধারণ গোসলখানায় প্রবেশ কর? আমি রাসূলে করীম (সা)-কে বলতে শুনেছি, যে নারী তার স্বামীর ঘর ছাড়া অন্য কোথাও তার কাপড় খুলে ফেলে সে তার ও তার আল্লাহর মধ্যকার পর্দাকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলে।
হযরত উম্মে সালমা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা) বলেছেনঃ (আরবী****************)
যে নারী তার নিজের ঘর ছাড়া অন্যত্র স্বীয় পরিধানের কাপড় খুলে ফেলে আল্লাহ্ তার পর্দাকে ছিন্নভিন্ন করে দেন। (আহমদ, তাবরানী, হাকেম)
সাধারণ গোসলখানায় মেয়েদের প্রবেশ পর্যায়ে ইসলামের যখন এতটা কড়াকড়ি অথচ তা চার দেওয়াল পরিবেষ্টিত ও তাতে কেবল নারীরাই প্রবেশ করে, তখন সেই নির্লজ্জ ও ভবঘুরে মেয়েদের সম্পর্কে কি বলা হবে, যারা রাস্তাঘাটে নিজেদের লজ্জাস্থান উন্মুক্ত করে বেড়ায়, মধু আহরণকারীদের লালসা উত্তেজিত করে তোলে, সমুদ্রতীরে নিজেদের দেহের প্রদর্শনী করে, লোভাতুর কামাতুর দৃষ্টিগুলোর জন্যে দর্শন স্বাদ গ্রহণের ব্যবস্থা করে ও যৌন আবেগকে উত্তেজিত করার কাজে সদা লিপ্ত থাকে?....... আসলে এরা তাদের ও মহান আল্লাহর মধ্যে রক্ষিত লজ্জা-শরমের সব আড়াল আবডালকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলেছে। পুরুষরাও এ গুনাহে সমানভাবে শরীক। কেননা তাদের তো দায়িত্বশীল ও রক্ষণাবেক্ষণকারী নিযুক্ত করা হয়েছে নারীদের জন্যে।........হায়! পুরুষদের কাণ্ডজ্ঞান কি কোন দিনই ফিরে আসবে না?
নারীদের উলঙ্গতা-উচ্ছৃঙ্খলতা হারাম
মুসলিম নারী কাফির কিংবা জাহিলিয়াতের যুগের নারীদের থেকে স্বতন্ত্র ও ভিন্নতর চরিত্রের অধিকারিনী হয়ে থাকে। নৈতিক চরিত্র, পবিত্রতা, সতীত্ব ও লজ্জা-শরমের সভ্রম রক্ষা করাই মুসলিম নারীদের বিশেষত্ব।
পক্ষান্তরে জাহিলী নারীর চরিত্র হচ্ছে নগ্নতা-উচ্ছৃঙ্খলতা ও পুরুষদের মধ্যে যৌন উত্তেজনা জাগিয়ে তোলার দক্ষতা দেখান। কুরআনে ব্যবহৃত শব্দ (আরবী****************) অর্থঃ খুলে যাওয়া, উন্মুক্ত হওয়া প্রকাশিত হওয়া, প্রকাশিত হয়ে পড়া। সাধারণ লোকদের দেখতে পারা। এ সাদৃশ্যের কারণে আরবী ব্যবহার হচ্ছেঃ (আরবী****************)
এ জন্যে যে, আকাশমণ্ডল সুউচ্চে অবস্থিত এবং তা দৃষ্টিমানের সম্মুখে প্রকাশিত।
আল্লামা যামাখশারী বলেছেন (আরবী****************) শব্দের নিঘূঢ় তত্ত্ব হচ্ছে, যা গোপন রাখা কর্তব্য তাকে বিশেষ যত্ন ও ব্যবস্থাপনা সহকারে প্রকাশ করে দেয়া। আরবী কথন হচ্ছেঃ (আরবী****************) ‘প্রকাশমান নৌকা’- কেননা তার ওপর কোন পর্দা নেই। এ অর্থের সামঞ্জস্যের কারণে নারীর পুরুষদের জন্যে আবরনমুক্ত ও উলঙ্গ হওয়া অর্থে এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা এ করে নারী তার সমস্ত সৌন্দর্য ও দৈহিক লালিমা কান্তি পুরুষের সম্মুখে উন্মুক্ত করে দেয়। ইমাম যামাখশারী এ অর্থে একটা নতুন দিকে ইঙ্গিত করেছেন, তা হচ্ছে উদ্যোগ-আয়োজন করে গোপনীয় জিনিসকে প্রকাশ করে দেয়া অথচ তা গোপন করে রাখাই বাঞ্ছনীয় ছিল। দেহের বিশেষ বিশেষ অঙ্গ, অঙ্গ-প্রত্যাঙ্গের হেলানো-দোলানো, কথা বলার ও চলার বিশেষ ধরন ও ভঙ্গি বা অলংকারাদি এসব ভিন্ পুরুষের সম্মুখে প্রকাশ করাই ‘তাবাররুজ’।
এ ‘তাবাররুজ’ –এর বিভিন্ন রূপ ও ভঙ্গি রয়েছে, প্রাচীনকালের লোকেরা যেমন তা জানত, এ কালের লোকদেরও তা ভালভাবে জানা। কুরআনের নিম্নোদ্ধৃত আয়াতের তাফসীরকারগণ তার উল্লেখ করেছেনঃ (আরবী****************)
হে মেয়েরা! তোমরা তোমাদের ঘরে স্থিতি গ্রহণ করে থাক এবং প্রাচীন জাহিলিয়াতের সময়ের মতো প্রদর্শনী করে বেড়িও না।
মুজাহিদ বলেছেনঃ তখন মেয়েরা লীলায়িত ভঙ্গিতে চলাফেরা করত।
মুকাতিল বলেছেনঃ মেয়েরা তাদের ওড়না মাথার ওপর রাখত, কিন্তু শক্ত করে বাঁধত না। ফলে গলার হার, কানের বালা ও গলা-গ্রীবা উন্মুক্ত হয়ে যেত।
প্রাচীন জাহিলী যুগের এই ছিল ‘তাবাররুজ’ অর্থাৎ পুরুষদের সাথে মাখামাখি ব্যাপকভাবে হতো। চলনে বলনে বিশেষ লাস্যতা দেখা যেত। নারীর ওড়না এমনভাবে ব্যবহৃত হতো যে, তার দেহ ও অলংকারের সৌন্দর্য প্রকাশ হয়ে পড়ে। কিন্তু আধুনিক জাহিলিয়াত এমন সব ভঙ্গি ও বৈচিত্র্য অর্জন করেছে যে, তাতে প্রাচীন জাহিলিয়াতকে অনেক পিছনে ফেলে দিয়েছে।
কোন্ অবস্থায় ‘তাবাররুজ’ হয় না
নিম্নোদ্ধৃত নিয়মাবলী পালন করে চললে মুসলিম নারী ‘তাবাররুজ’ –এর সীমা ত্যাগ করে ইসলামী সভ্যতার পরিবেশে অনুপ্রবেশ করতে পারেঃ
(ক) দৃষ্টি নত রাখা- কেননা লজ্জা-শরমই হচ্ছে নারীর সবচাইতে অধিক মূল্যবান সৌন্দর্য। আর লজ্জা-শরমের বড় প্রকাশ পাওয়া যায় দৃষ্টি নত রাখার মাধ্যমে। তাই আল্লাহ্ বলেছেন এ ভাষায়ঃ (আরবী****************)
এবং বল ঈমানদার মহিলাদের, তারা যেন তাদের দৃষ্টির একাংশ নত রাখে।
(খ) পুরুষদের সাথে নিবিড় ঘনিষ্ঠতা এড়িয়ে চলতে হবে- এ কালের সিনেমা হল, মিটিং-জনসভা ও হোটেল-রেস্তোরা ও কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস কক্ষ ও করিডোরে-কেন্টিনের ভিড়ে এ মাখামাখিটা পুরামাত্রায় লক্ষ্য করা যায়। হযরত মা’কাল ইবনে ইয়াসার (রা) রাসূলে করীম (সা)-এর বাণী বর্ণনা করেছেনঃ (আরবী****************)
যে স্ত্রীলোকটি হালাল নয়, তাকে স্পর্শ করা অপেক্ষা নিজের মাথায় লৌহ শলাকা বসিয়ে দেয়া অনেক উত্তম। (তিবরানী, বায়হাকী)
(গ) তার পোশাক-পরিচ্ছেদ ইসলামী শরীয়তের আদব-কায়দা ও নিয়ম-নীতি সম্মত হতে হবে- আর শরীয়তসম্মত পোশাক বলতে বোঝায় তা, যাতে নিম্নোদ্ধৃত গুণাবলী রয়েছেঃ
১. সমস্ত দেহ আবৃত করে, কুরআন নিজেই (আরবী****************) ‘যা স্বতঃই প্রকাশ হয়ে পড়ে’ বাদ দিয়েছে, তা ছাড়া- অর্থাৎ মুখমণ্ডল ও পাঞ্জাদ্বয় ব্যতীত সমস্ত শরীর ঢাকতে হবে।
২. কাপড়ের অভ্যন্তর থেকে দেহ বা দেহের কান্তি দৃশ্যমান হতে পারবে না। নবী করীম (সা) জানিয়ে দিয়েছেনঃ (আরবী****************)
যে সব মেয়েলোক কাপড় পরেও ন্যাংটা, পুরুষদের প্রতি আকৃষ্ট এবং পুরুষদেরও আকৃষ্টকারী, তারা জাহান্নামী, তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না এবং জান্নাতের সুঘ্রাণও কিছু পাবে না।
পোশাক পরেও যদি পোশাক পরার উদ্দেশ্য- শরীর আবৃতকরণ- অপূর্ণ থেকে যায়, কাপড় খুব পাতলা হওয়ার দরুন দেহের সব কিছুই বাইরে থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠে, তাহলেই কাপড় পরেও ন্যাংটা থাকা হয়।
বনু তামীম গোত্রের কিছু সংখ্যক মেয়েলোক হযরত আয়েশা (রা)-এর কাছে উপস্থিত হয়। তাদের পরনে খুবই পাতলা কাপড় ছিল। তা দেখে হযরত আয়েশা (রা) বললেনঃ (আরবী****************)
তোমরা যদি ঈমানদার হয়ে থাক, তাহলে জেনে রাখ, এটা মুমিন মহিলাদের পোশাক নয়, যা তোমরা পরেছ।
একটি বিয়ের কনে হযরত আয়েশা (রা)-এর কাছে উপস্থিত হলো। তার পরিধানে ছিল খুবই স্বচ্ছ পাতলা কাপড়। তখন তিনি বললেনঃ (আরবী****************)
যে ব্যক্তি এ ধরনের পোষাক পরিধান করে, সে সূরা আন-নূরে বিধৃত বিধানের প্রতি ঈমান আনে নি।
৩. পোশাক এমন আটসাট হবে না, যার দরুন দেহের উচ্চ-নীচ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সবই বাইরে দৃশ্যমান হয়ে উঠে, যদিও তা স্বচ্ছ পাতলা নয়। পাশ্চাত্য-সভ্যতা যে পোশাকের প্রবর্তন করেছে, তা এ পর্যায়ের বড় নিদর্শন। এ সভ্যতা দেহ ও যৌনতার পূজারী, এ সভ্যতার প্রভাবে ফ্যাশন-উদ্ভাবনকারীরা এমনভাবে কাপড় কাটে যে, স্তনদ্বয়, নিতম্ব ও উরুদ্বয় প্রভৃতি যৌনাঙ্গসমূহ দর্শকদের সম্মুখে প্রকটভাবে ভেসে উঠে। সে পোশাক এমন ঢং-এ বানান হয় যে, তাতে যৌন আবেগে আলোড়নের সৃষ্টি হয়। এ ধরনের পোশাক পরিধানকারী নারীও ‘কাপড় পরা সত্ত্বেও ন্যাংটার মধ্যে গণ্য’- এ কাপড় ও পোশাক স্বচ্ছ ও পাতলা কাপড় অপেক্ষাও অনেক বেশি বিপদের আহবানকারী।
৪. পুরুষদের জন্যে নির্দিষ্ট পোশাক মেয়েরা পরবে না। যেমন কোন পাতলুন। এটা এ কালের পুরুষদের জন্যে নির্দিষ্ট বিশেষ পোশাক। কেননা নবী করীম (সা) পুরুষদের সাথে সাদৃশ্য সৃষ্টিকারী নারীদের ওপর অভিশাপ বর্ষণ করেছেন, যেমন অভিশাপ দিয়েছেন সেসব পুরুষদের ওপর যারা মেয়েদের সাথে সাদৃশ্য সৃষ্টি করে। এ জন্যেই নবী করীম (সা) মেয়েদেরকে পুরুষদের পোশাক পরতে নিষেধ করেছেন এং পুরুষদের নিষেধ করেছেন মেয়েদের পোশাক পরতে।
৫. ইয়াহূদী, খ্রিস্টান, অগ্নিপূজারী, কাফির মেয়েদের বিশেষ বিশেষ পোশাকও পরবে না। কেননা ওদের সাথে সাদৃশ্য করতে ইসলামে নিষেধ করা হয়েছে। পুরুষ ও নারীর মধ্যে যেমন পার্থক্য করতে চায় ইসলাম, তেমনি বাইরে ও অন্তরে কাফির জাতিগুলোর অন্ধ অনুসরণ করা থেকেও মুক্তি কামনা করে। এ কারণেই বহু বহু ব্যাপারে কাফিরদের বিরোধিতা করার জন্যে ইসলাম সুস্পষ্ট ভষায় নির্দেশ দিয়েছে। রাসূলে করীম (সা) নিম্নোদ্ধৃত বাণীটি এ পর্যয়েরঃ (আরবী****************)
যে লোক অপর যে-জাতির সাথে সাদৃশ্য করবে, সে তাদের মধ্যেই গণ্য হবে।
(ঘ) চলাফেরা ও কথাবার্তায় তাকে গাম্ভীর্য ও দৃঢ়তা অবলম্বন করতে হবে। তার দেহের ও মুখমণ্ডলের সমস্ত গতিবিধি ফেরানো ঘোরানোয় যৌন আবেগকে উত্তেজিত করণ থেকে পূর্ণমাত্রায় বিরত থাকতে হবে। কেননা চলাফেরা কথাবার্তায় লাস্যতা ও লীলাময়তা চরিত্রহীন কাফির মেয়েদের বিশেষত্ব, মুসলিম মহিলাদের চরিত্র নয়। আল্লাহর এ কথাটি এ পর্যায়ে পুনঃ পঠনীয়ঃ (আরবী****************)
নিম্ন নম্র কণ্ঠস্বরে কথা বলবে না, বললে অন্তরের রোগ সম্পন্ন ব্যক্তি লালায়িত হয়ে পড়বে। (সূরা আহযাবঃ ৩২)
(ঙ) সুগন্ধি, আতর-স্নো-পাউডার ইত্যাদির দ্বারা স্বীয় গোপন সৌন্দর্যের প্রতি পুরুষদের মনে আকর্ষণ সৃষ্টি করতে পারবে না। আল্লাহ্ বলেছেনঃ (আরবী****************)
মাটিতে পা শক্তভাবে ফেলে চলবে না, কেননা তা করা হলে যে রূপ-সৌন্দর্য-অলংকার তারা লুকিয়ে রেখেছে, তা তারা জেনে যাবে।
জাহিলিয়াতের যমানায় মেয়েরা যখন লোকদের মধ্যে চলাফেরা করত তখন তারা নিজেদের পা ঝনাৎ করে মাটিতে ফেলত। ফলে পায়ের অলংকার ঝংকার দিয়ে উঠত ও লোকেরা সে ধ্বনি শুনতে পেত। এ কারণে কুরআনে তা করতে নিষেধ করেছে। কেননা এরূপ করা হলে লালসা-কাতর পুরুষদের মনে যৌন চিন্তা-ভাবনা তীব্র হয়ে জেগে উঠবে। সে নারী সম্পর্কে সে ভাবতে শুরু করবে যে, এ নারী পুরুষদেরকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করতে ইচ্ছুক।
বিভিন্ন সুগন্ধি মেখে বায়ু পরিমণ্ডল ভারাক্রান্ত করে তুলে, যৌন আবেগকে উত্তেজিত করে ও পুরুষদের নিজেদের প্রতি আকৃষ্ট করতে চেষ্টা করে যেসব মেয়ে, তাদের সম্পর্কেও এ কথাই প্রযোজ্য। হাদীসে বলা হয়েছেঃ (আরবী****************)
মেয়েলোক আতর-সুগন্ধি মেখে সভা-মজলিসে উপস্থিত হলে সে এই-এই অর্থাৎ জ্বেনাকারী। (আবী দাঊদ, তিরমিযী)
এই বিস্তারিত আলোচনা থেকে আমরা নিঃসন্দেহে জানতে পারলাম যে, মেয়েরা ঘরের ‘কারাগারে’ (?) বন্দী হয়ে পড়ে থাকুক এবং কবর ছাড়া আর কোন স্থানে বের হয়ে না যাক, ইসলাম সে বাধ্যবাধকতা আদৌ আরোপ করেনি। বরং নামাযের জামাতে শরীক হওয়া, জ্ঞান শিক্ষা লাভ ও অন্যান্য জৈবিক ও পারিবারিক প্রয়োজন পূরণার্থে ঘরের বাইরে যাওয়া মুসলিম মহিলাদের জন্যে সম্পূর্ণ জায়েয। সাহাবী মহিলা ও তাঁদের পরবর্তী কালের মুসলিম মহিলাগণ তা-ই করতেন। তাঁদের অনেকে যুদ্ধে শরীক হওয়ার জন্যেও বের হয়েছেন। রাসূলে করীম (সা)-এর সঙ্গেও বের হয়েছেন। তাঁর পরে খলীফা ও ইসলামী সেনাধ্যক্ষের সঙ্গেও বাইরে গেছেন। নবী করীম (সা) তাঁর বেগম হযরত সাওদা (রা)-কে বলেছেনঃ (আরবী****************)
আল্লাহ্ তোমাদের অনুমতি দিয়েছেন, তোমরা তোমাদের প্রয়োজনে ঘরের বাইরে যেতে পার। (বুখারী)
তিনি আরও বলেছেনঃ (আরবী****************)
তোমাদের কোন স্ত্রী যদি তোমাদের কাছে মসজিদে নামাযে যাওয়ার জন্যে অনুমতি চায়, তাহলে তাকে যেন নিষেধ না কর। (বুখারী)
অপর এক হাদীসে বলা হয়েছেঃ (আরবী****************)
তোমরা আল্লাহর দাসীদেরকে মসজিদে যেতে নিষেধ করবে না। (মুসলিম)
কোন কোন আলিম এ পর্যায়ে খুবই কঠোরতা করে থাকেন। তাঁদের মতে ভিন্ পুরুষ-দেহের কোন একটি অংশের ওপরও নজর দেয়া স্ত্রীলোকদের জন্যে হারাম। তাঁরা দলিল হিসেবে উম্মে সালমা (রা)-এর দাস নরহান বর্ণিত একটি হাদীস পেশ করেন। হাদীসটি হচ্ছেঃ (আরবী****************)
হযরত উম্মে সালমা ও মায়মুনার ঘরে আবদুল্লাহ্ ইবনে উম্মে মাকতুম প্রবেশ করলে নবী করীম (সা) তাদের দুজনকে বললেনঃ তোমরা পর্দা কর। তাঁরা বললেনঃ ও তো অন্ধঃ নবী করীম (সা) বললেন, তোমরা দুজনও কি অন্ধ? তোমরা দুজনও কি দেখতে পাও না?
কিন্তু বিশেষজ্ঞগণের মতে এ হাদীসটি সহীহ্ নয়। কেননা এ হাদীসের বর্ণনাকারী নরহান উম্মে সালমার দাস, তার হাদীস দলিল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়।
আর যদি হাদীসটি সহীহ হয়ও তবু বলতে হবে, এটা হচ্ছে নবী করীম (সা)-এর তাঁর বেগমদের জন্যে তাঁদের মান-মর্যাদার দৃষ্টিতে অতিরিক্ত কড়াকড়ি। পর্দার ব্যাপারে তাঁদের প্রতি রাসূলে করীমের এ কড়াকড়ি ছিল। আবূ দাঊদ প্রমুখ হাদীস বিশারদ এ দিকে ইঙ্গিতও করেছেন। কাজেই সহীহ্ প্রমাণিত হাদীসই দলিল হিসেবে অবশিষ্ট থাকল। আর তা হচ্ছেঃ (আরবী****************)
নবী করীম (সা) ফাতিমা বিনতে কায়স (রা)-কে উম্মে সুরাইকের ঘরে ইদ্দত পালনের নির্দেশ দিলেন, কিন্তু পরে তিনি এ নির্দেশ সংশোধন করে বললেনঃ ও মেয়েলোকটিকে আমার সাহাবীরা ভয় করেন। তার চাইতে বরং তুমি ইবনে উম্মে মকতুমের কাছ থেকে ইদ্দত পালন কর। কেননা সে অন্ধ ব্যক্তি। তুমি কাপড় ছাড়বে, কিন্তু সে তোমাকে দেখতে পাবে না। (কুরতুবী)
স্ত্রীর স্বামীর মেহমানদের খেদমত করা
এ পর্যন্তকার আলোচনা থেকে একথাও স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, স্বামীর উপস্থিতিতে, তার মেহমানদের খেদমতের কাজ স্ত্রী করতে পারে। তবে সেজন্য শর্ত হচ্ছে- তার পোশাক, সৌন্দর্য-অলংকার ও কথাবার্তা, চালচলন ইত্যাদি ইসলামী নিয়ম-নীতি ও সভ্যতা ভব্যতার অনুকূল হতে হবে। এমতাবস্থায় মেহমান পুরুষ তাকে (স্ত্রীকে) দেখবে এবং সেও দেখবে তাদের, এটা অতি স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু তাতে কোন দোষ হবে না। কেননা এ ক্ষেত্রে কোন পক্ষ থেকেই কোনরূপ সীমালংঘন বা বিপদ সঙ্ঘটিত হওয়ার কোন আশংকা নেই।
হযরত সহল ইবনে সায়াদ আল-আনসারী (রা) বর্ণনা করেছেনঃ (আরবী****************)
আবূ উসাইদ সায়েদী বিবাহ উপলক্ষে নবী করীম (সা) ও তাঁর সাহাবিগণকে আহবান করলেন। এ উপলক্ষে রান্না-বান্না করে খাবার প্রস্তুত করা ও তা পেশ করার কাজ তাঁর স্ত্রী উম্মে উসাইদ সম্পন্ন করলেন। পাথরের একটি পাত্রে কিছু খেজুর রাত থেকেই ভিজাবার জন্যে রেখে দিলেন। নবী করীম (সা) খাবার খেয়ে নিলে পর তা নিজ হাতে খুলে নবী করীম (সা)-এর কাছে তা পান করার জন্যে তোহফা স্বরূপ পেশ করলেন। (বুখারী, মুসলিম)
ইবনে হাজার আল-আসকালানী যেমন বলেছেন, এ হাদীস থেকে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় যে, স্বামীর মেহমান ও নিমন্ত্রিত লোকদের খেদমতের জন্যে স্ত্রীর অগ্রসর হওয়া তা তাদের সামনে উপস্থিত হওয়া সম্পূর্ণ জায়েয। তবে বলাই বাহুল্য যে, তা করা যাবে যদি কোন নৈতিক বিপদের আশঙ্কা না থাকে তবে। এ সময় দেহকে পূর্ণ মাত্রায় আবৃত রাখতে হবে। এরূপ অবস্থায় স্বামীর পক্ষে স্ত্রীর দ্বারা মেহমানদের খেদমত ও খাবার পরিবেশন করার কাজ করান জায়েয। কিন্তু স্ত্রী যদি দেহ আবৃতকরণ পর্যায়ে ইসলামের ধার্য করা নিয়ন্ত্রণ ও বাধ্যবাধকতা রক্ষা না করে- বর্তমানে যেমন প্রায়শ দেখা যায়- তাহলে পুরুষদের সম্মুখে আসা স্ত্রীর জন্যে জায়েয নয়।
প্রকৃতি বিরোধী কাজ কবীরা গুনাহ
যৌন কামনা-বাসনা নিয়ন্ত্রণের ও সংগঠনের যে পন্থা ইসলাম গ্রহণ করেছে, সেই পর্যায়ে একটি জরুরী কথা হচ্ছে, ইসলামে জ্বেনা ও তার উপায় ও কারণসমূহ যেমন হারাম, তেমনি ‘লেওয়াতাত’ বা লুত জাতি’র প্রকৃতি পরিপন্থী কাজকেও সম্পূর্ণ হারাম করে দেয়া হয়েছে।
এ জঘন্য ও বীভৎস কার্য যেমন প্রকৃতি-বিরোধী, কলঙ্ক-কালিমা লেপনকারী, পৌরুষ খর্বকারী, তেমনি নারীর অধিকার হরণের অপরাধও বটে এবং সেজন্যে তা একটা বড় জুলুম।
যে সমাজেই এ জঘন্য কাজের প্রসারতা হবে, সে সমাজের জন-জীবন চরম বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে যাবে। তারা এ কুৎসিত কাজে অভ্যস্ত হয়ে তার দাসে পরিণত হবে। তাছাড়া চরিত্র, সুস্থ রুচি ও পবিত্রতা- সব কিছুই হারিয়ে ফেলবে। এ পর্যয়ে কুরআনে বিধৃত লূত জাতির কিসসাই সঠিক জ্ঞান লাভের জন্যে যথেষ্ট। এ জাতির লোকেরা এহেন জঘন্য ও বীভৎস কাজ শুরু করে তার ব্যাপক প্রচলন করেছিল। বৈধ ও পবিত্র স্ত্রীদের তারা ত্যাগ করেছিল এবং এ হারাম কার্য অবলম্বন করেছিল। এ কারণে আল্লাহর নবী হযরত লূত (আ) তাদের বললেনঃ (আরবী****************)
দুনিয়ার মধ্যে কেবল তোমরাই এমন যে, তোমরা পুরুষদের কাছে যাও। আর তোমাদের জন্যে যে স্ত্রীদের আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন, তাদের পরিত্যাগ করছ? বরং তোমরা তো সীমালংঘনকারী লোক। (সূরা শূ’আরাঃ ১৬৫-১৬৬)
কুরআন মজীদ এ কাজকে প্রত্যাখ্যান করেছে, এ কাজকে জুলুম, বাড়াবাড়ি, মূর্খতা, বিপর্যয় ও অপরাধ বলে ঘোষণা করেছে। এটা মানব স্বভাবের চরম বিকৃতি, হেদায়েতের পথ থেকে চরম বিভ্রান্তি। নৈতিকতার চরম বিপর্যয় ও রুচির মারাত্মক অসুস্থতা। এ লোকদের পরীক্ষার জন্যে আল্লাহ্ তা’আলা মানুষের আকৃতিতে ফেরেশতাদের পাঠিয়েছিলেন। এদের প্রতি জাতির জনগণ যে আচরণ গ্রহণ করেছিল, তার প্রতিশোধ স্বরূপ আল্লাহ্ তাদের ওপর কঠিন আযাব নাযিল করেন। কুরআনে তাই বলা হয়েছেঃ (আরবী****************)
আমাদের ফেরেশতাগণ যখন লূত-এর কাছে পৌঁছল, তাদের আগমনে সে ঘাবড়ে গেল, মনটা খারাপ হয়ে গেল। বলতে লাগল, আজ বড় বিপদের দিন। এ মেহমানদের আগমনে তার জাতির লোকেরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে তার ঘরের দিকে দৌড়ে এল। পূর্ব থেকেই তারা এরূপ দুষ্কৃতি ও জঘন্য কাজে অভ্যস্ত ছিল। লূত তাদের বললঃ ভাইরা আমার মেয়েরা রয়েছে, ওরাই তোমাদের জন্যে পবিত্রতর। আল্লাহকে অবশ্য ভয় করবে, আর আমার মেহমানদের ব্যাপারে আমাকে লজ্জিত কর না। তোমাদের মধ্যে সমঝদার ব্যক্তি কি কেউ নেই? তারা জবাবে বললঃ তোমার তো জানাই আছে যে, তোমার মেয়েদের ক্ষেত্রেও আমাদের কোন অংশ নেই। তুমি এ-ও জান যে, আমি তোমাদের শায়েস্তা করে দিতে পারতাম কিংবা কোন সুদৃড় সহায়ই হতো যার আশ্রয় আমি গ্রহণ করতাম। তখন ফেরেমতাগণ তাঁকে বললঃ হে লূত! আমরা তো তোমার আল্লাহর প্রেরিত ফেরেশতা। এ লোকেরা তোমার কোন ক্ষতিই করতে পারবে না। (সূরা হুদঃ ৭৭-৮১)
এ দুষ্কৃতি ও জঘন্য কাজ যে করবে, তাকে কি শাস্তি দেয় যেতে পারে, তা নিয়ে ফিকাহবিদদের মধ্যে বিভিন্ন মত রয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে লেওয়াতাতকারীকে কি জ্বেনাকারীর দণ্ড দেয়া হবে কিংবা লেওয়াতাতকারী ও যার সাথে তা করা হয়েছে এ উভয়কে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে- হত্যা করা হবে? আর হত্যা করা হলে তাকে কি দিয়ে হত্যা করা হবে, তরবারি দ্বারা কিংবা আগুনে জ্বালিয়ে মারা হবে? অথবা উচ্চ প্রাচীরের ওপর থেকে ফেলে দিয়ে মারা হবে?
এ ধরনের অপরাধের ব্যাপারে ইসলামের এ কঠোরতাকে নির্মমতা মনে করা যেতে পারে। কিন্তু ইসলামী সমাজবে এ ধরনের পংকিল ও কদর্য কার্যকলাপ থেকে পবিত্র রাখা এরূপ কঠোর শাস্তি প্রয়োগ ছাড়া কিছুতেই সম্ভব নয়। কেননা এ গুনাহ, সংক্রামক, ক্ষতিকর। এ গুনাহ্ সমাজে প্রচলিত হলে ধ্বংস আর ধ্বংস ছাড়া অন্য কোন পরিণতিই হতে পারে না।
হস্তমৈথুন
অনেক যুবক যৌন উত্তেজনা দমনের উদ্দেশ্যে নিজ হস্তদ্বয়ের আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে। নিজ হাতের মৈথুনের সাহায্যে শুক্র নিষ্কাশন করে স্নায়ূমণ্ডলীকে শান্ত করে থাকে। অধুনা এক ‘গোপন স্বভাব’ নামে অভিহিত করা হয়।
অনেক বিশেষজ্ঞই এ কাজকে হারাম বলেছেন। ইমাম মালিক এ ব্যাপারে কুরআন মজীদের নিম্নোদ্ধৃত আয়াতকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করেছেনঃ (আরবী****************)
আর যারা তাদের যৌন অঙ্গের সংরক্ষণ করে- তাদের স্ত্রীদের ও দাসীদের ছাড়া-তাদের প্রতি কোন তিরস্কার নেই। এর বাইরে অন্য কোন পন্থা যারাই অবলম্বন করবে, তারাই আসলে সীমালংঘনকারী। (সূরা মুমিনূনঃ ৪-৭)
ইমাম মালিকের মতে- যারা হস্তমৈথুন করে, তারা কুরআন ঘোষিত বৈধ পন্থা বাদ দিয়ে ভিন্নতর পন্থার আশ্রয় গ্রহণ করে। অতএব তা হারাম।
ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল থেকে বর্ণিত, তিনি শুক্রকে দেহের অপরাপর আবর্জনার মতোই এক আবর্জনা বিশেষ মনে করতেন। আর উপরিউক্ত উপায়ে তাঁর বহিস্কারকরণকে জায়েয মনে করতেন। যেমন ‘সিন্তা’ লাগান। ইমাম ইবনে হাজমও এ মত সমর্থন করেছেন। হাম্বলী মাযহাবের আলিমগণ দুই শর্তে এ কাজকে জায়েয বেলেছেন। একটি হলো, তা করা না হলে জ্বেনাকারীতে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা হওয়া আর দ্বিতীয় হচ্ছে, বিয়ে করতে অক্ষম হওয়া।
এ প্রেক্ষিতে আমরা ইমাম আহমদের মত গ্রহণ করতে পারি কেবল সে অবস্থায়, যখন যৌন উত্তেজনা অদম্য হয়ে উঠবে এবং তার দরুন জ্বেনা ব্যভিচার করে বসতে পারে এ ভয় তীব্র হয়ে উঠবে। যেমন শিক্ষারত ছাত্র ও বিদেশে কর্মরত নিঃসঙ্গ ব্যক্তি। আর তার সম্মুখে যদি বিদ্যমান থাকে যৌন উত্তেজনার অসংখ্য কারণ। এরূপ অবস্থায় যে কোন ব্যক্তির পক্ষে আত্মসংযম করে থাকা খবই কঠিন ও দুষ্কর হয়ে পড়ে। এ ধরনের ব্যক্তির পক্ষে আত্মসংযম করে থাকা খুবই কঠিন ও দুষ্কর হয়ে পড়ে। এ ধরনের ব্যক্তির পক্ষে তার যৌন উত্তেজনা দমন করার জন্যে এ উপায় অবলম্বন করা খুব বেশি দোষের হবে না। তবে তাতেও শর্ত এই যে, এ কাজে সীমা ছাড়িয়ে যাওায়া এবং এ পন্থাকে স্থায়ীভাবে গ্রহণ করা কিছুতেই জায়েয হবে না।
তবে নবী করীম (সা) বিবাহ করতে অসমর্থ মুসলিম যুবকদের সে পথ দেখিয়েছেন, তাই সর্বোত্তম পন্থা। তা হচ্ছে তার উচিত বেশি বেশি রোযা রাখা। কেননা রোযা মানুষের ইচ্ছাশক্তিকে সুসংযত ও সুসংহত করে। ধৈর্য শিক্ষা দেয়, ধৈর্যধারণে অভ্যস্ত করে তোলে। রোযা মানুষের মধ্যে তাকওয়ার শক্তিকে বাড়িয়ে দেয়, আল্লাহকে হাযের-নাজের জানার ভাবধারাকে প্রবল করে তোলে। এ পর্যায়ে নবী করীম (সা)-এর বাণী হেচ্ছেঃ (আরবী****************)
হে যুবক সমাজ! তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রী সঙ্গমে সক্ষম তাদের বিয়ে করা বর্তব্য। কেননা এ বিয়ে তাকে চক্ষু নত রাখতে অভ্যস্ত করবে এবং তার যৌন অঙ্গকে পবিত্র ও সুরক্ষিত রাখবে। আর যে যুবক বিয়ে করতে অসমর্থ হবে, তার রোযা রাখা উচিত। কেননা এ রোযাই তার ঢালস্বরূপ হবে।
ইসলামে বৈরাগ্যবাদ নেই
ইসলামে যৌন উত্তেজনাকে লাগামমুক্ত ও অবাধ করে দেয়া হয়ন। কেননা তা করে দেয়া হলে তা কোন সীমা বা বাধা-বন্ধন, শর্ত-প্রতিবন্ধকতা মেনে চলতে প্রস্তুত হবে না। এ কারণেই জ্বেনা-ব্যভিচার এবং তৎসংশ্লিষ্ট ও সেদিকে টেনে নেয়ার যাবতীয় কার্যক্রমকেও হারাম করে দেয়া হয়েছে। অপরদিকে এ স্বভাবজাত প্রবণতার সাথে সাংঘর্ষিক ও তাকে সমূলে উৎখাতকারী ভাবধারাকেও ইসলাম একবিন্দু সমর্থন করেনি। এ কারণেই ইসলাম বিবাহ করার উৎসাহ দিয়েছে এবং অবিবাহিত বা চিরকুমার হয়ে থাকা কিংবা নিজেকে নপুংসক বানানোর প্রচণ্ড বিরোধিতা করে। অতএব সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কোন মুসলিম পুরুষ বা নারীর বিয়ে না করে থাকা এ উদ্দেশ্যে যে, সে দুনিয়ার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে আল্লাহর জন্যে উৎসর্গীকৃত থাকতে চায় কিংবা সম্পূর্ণ নির্ঝঞ্ঝাট একমূখিতা নিয়ে আল্লাহর ইবাদতে মশগুল হয়ে থাকতে চায়-আদৌ জায়েয নয়। ইসলামে এরূপ মনোভাব বা কর্মনীতির একবিন্দু সমর্থন নেই।
রাসূলে করীম (সা)-এর কোন কোন সাহাবীর মধ্যে দুনিয়া ত্যাগের প্রবণতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল। কিন্তু নবী করীম (সা) যখনই তা টের পেলেন, তখনই ঘোষণা করে দিলেন যে, দুনিয়া ত্যাগ করা ইসলামী জীবনধারা পরিহার ও রাসূলের সুন্নাতকে অগ্রাহ্য করার শামিল। বস্তুত এ এক খ্রিস্টানসূলভ প্রবণতা। রাসূলে করীম (সা) এ প্রবণতাকে সম্পূর্ণ ইসলাম বিরোধী বলে ঘোষণা করলেন। আবূ কালাবা থেকে বর্ণিতঃ (আরবী****************)
কিছু সংখ্যক সাহাবী দুনিয়া ত্যাগ করার, স্ত্রী সংসর্গ বর্জন করার ও বৈরাগ্যবাদ অবলম্বন করার ইচ্ছা গ্রহণ করলেন। কিন্তু নবী করীম (সা) এ ব্যাপারটিকে খুব শক্তভাবে ধরলেন। বললেনঃ তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা দ্বীন পালনে চরম কঠোরতা ও কৃচ্ছ্রতা গ্রহণ করল, তখন আল্লাহও তাদের প্রতি কঠোরতা প্রয়োগ করলেন। এ কালের গির্জা-মঠ ও খানকাসমূহে অবস্থানকারী লোকেরা তাদেরই উত্তরাধিকারী। অতএব তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং কাউকেই তাঁর শরীক বানিও না। হজ্জ কর, উমরা কর আর সোজা ঋজু পথ অবলম্বন কর, তাহলে তোমাদের সাথে যথাযথ আচরণ করা হবে। (আব্দুর রাজ্জাক ইবনে জরির-ইবনে মুনযির)
এ হাদীসের বর্ণনাকারী বলেনঃ এ লোকদের সম্পর্কেই নিম্নোদ্ধৃত আয়াতটি নাযিল হয়েছেঃ (আরবী****************)
হে ঈমানদার লোকেরা! আল্লাহ্ তোমাদের জন্যে যেসব পবিত্র জিনিস হালাল করেছেন, তোমরা তা হারাম কর না। আর সীমালংঘন কর না কেননা আল্লাহ্ সীমালংঘনকারীদের আদৌ ভালবাসেন না। (সূরা মায়িদাঃ ৮৭)
মুজাহিদ বলেছেনঃ উসমান ইবনে মজয়ূন ও আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর প্রমুখ সাহাবী স্ত্রী সংসর্গমুক্ত জীবন যাপন করার, নিজেদের ‘খাসি’ বানানর এবং চট বস্ত্র পরিধান করার সংকল্প গ্রহণ করলেন। পূর্বোদ্ধৃত ও তৎপরবর্তী আয়াত এ পর্যায়েই নাযিল হয়েছিল।
একদল সাহাবী কবী করীম (সা)-এর ঘরে উপস্থিত হয়ে তাঁর ইবাদত-বন্দেগী সম্পর্কে তাঁর বেগমদের কাছ থেকে জানতে চেষ্টা করতে লাগলেন। তাঁরা যখন যা জানবার জেনে নিলেন, তখন তাঁদের কাছে তা খুবই স্বল্প ও অপর্যপ্ত মনে হলো। তখন তাঁরা নিজেরাই বলতে লাগলেনঃ (আরবী****************)
রাসূলে করীমের সাথে আমাদের কি তুলনা হতে পারে? আল্লাহই তাঁর আগের ও পরের সব গুনাহ মাফ করে দিয়েছেন। অতঃপর তাদের একজন বললঃ আমি তো সারাটিকাল ধরে রোযা রাখব, রোযা ভঙ্গ করব না। দ্বিতীয় জন বললঃ আমি সারারাত জাগ্রত থেকে ইবাদত করব, একটুও ঘুমাব না। তৃতীয় জন বললঃ আমি নারী সংসর্গ বর্জন করে চলব, কখনই বিয়ে করব না। পরে নবী করীম (সা) যখন এ সংবাদ জানতে পারলেন, তখন তিনি তাঁদের ভুল ধারণা ও তাদের অবলম্বিত নীতির বক্রতা ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিলেন। তিনি বললেনঃ আল্লাহ্ সম্পর্কে আমি তোমাদের চেয়ে বেশি জানি, তোমাদের আপেক্ষা আমি তাঁকে ভয়ও করি বেশি। তা সত্ত্বেও আমি যেমন রাত জাগরণ করে ইবাদত করি তেমনি ঘুমাইও। আমি রোযাও থাকি, রোযা ভাঙ্গিও, আর স্ত্রী গ্রহণ করে দাম্পত্য জীবনও যাপন করছি। এই হচ্ছে আমার নীতি ও আদর্শ। অতএব যে তা পরিহার করবে, সে আমার উম্মতের মধ্যে গণ্য নয়।
হযরত সা’দ ইবনে আবূ ওয়াক্কাস (রা) বলেছেনঃ (আরবী****************)
উসমান ইবনে মজয়ূন স্ত্রী সংসর্গহীন জীবন গ্রহণ করতে চাইলে রাসূলে করীম (সা) তা প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি যদি তাঁকে অনুমতি দিতেন তাহলে আমরা খাসি করে নপুংসক হয়ে যেতাম।
এ প্রেক্ষিতেই বিশেষজ্ঞগণ মত দিয়েছেন যে, মুসলিম মাত্রেরই বিয়ে করা ফরয। সাধ-সামর্থ্য থাকা পর্যন্ত তা পরিহার করে চলা মাত্রই জায়েয নয়। অপরদের মতে যে লোক বিয়ে করতে ইচ্ছুক এবং তা না করলে নিজের চরিত্র রক্ষার ব্যাপারে আশংকা বোধ করে তার অবশ্যই বিয়ে করা উচিত।
অভাব-অনটন রিযকের অপ্রশস্ততা বা দায়িত্ব বোঝা বহনের সাহসহীনতার কারণে বিয়ে না করা কোন মুসলমানেরই শোভা পায় না। বরং তার উচিত আল্লাহর সাহায্য ও অনুগ্রহ লাভের জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করা। কেননা যারা নিজেদের চরিত্রের পবিত্রতা রক্ষার উদ্দেশ্যে বিয়ে করবে, আল্লাহ্ তাদের প্রতি অনুগ্রহ বর্ষণের ওয়াদা করেছেন। আল্লাহ্ তা’আলা ইরশাদ করেছেনঃ (আরবী****************)
তোমাদের মধ্যকার অবিবাহিত ব্যক্তিদের এবং তোমাদের দাস-দাসীদের মধ্যে যারা সচ্চরিত্র, তাদের বিয়ে দাও। তারা গরীব হলে আল্লাহ্ তাঁর অনুগ্রহ দিয়ে তাদের ধনী বানিয়ে দেবেন। (সূরা নূরঃ ৩২)
রাসূলে করীম (সা) বলেছেনঃ (আরবী****************)
তিন ব্যক্তির সাহায্য করা আল্লাহর দায়িত্ব। তারা হচ্ছেঃ নিজ চরিত্রের পবিত্রতা রক্ষার উদ্দেশ্যে বিবাহকারী, মনিবের সাথে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে মুক্তির চুক্তিকারী, যদি সে বাস্তবিকই সেই অর্থ দিতে ইচ্ছুক হয় এবং আল্লাহর পথে যোদ্ধা।
প্রস্তাবিত কনেকে দেখা
মুসলমান বিয়ে করার সংকল্প গ্রহণ করলে এবং কোন নির্দিষ্ট মেয়েকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিলে বিয়ে অনুষ্ঠানের পূর্বে তাকে প্রস্তাবকারীর দেখা শরীয়তসম্মত বিধান। এ দেখার কাজটা করা হলে সে বুঝে-শুনে সম্মুখে অগ্রসর হতে পারে। চোখ বন্ধ করে এ ধরনের কাজের দিকে অগ্রসর হওয়া কোনক্রমেই উচিত নয়। কেননা তাতে পরে অনুতাপ করার কারণ ঘটতে পারে ও নিজের মনেও হতাশা জাগতে পারে। এ ব্যবস্থাকে কার্যকর করা হলে তার কোন আশংকা থাকার কথা নয়।
বস্তুতঃ চোখ বা দৃষ্টি মনের প্রতিনিধিত্ব করে। ফলে দুজনের চক্ষুদ্বয়ের মিলনে দুজনের হৃদয়ে মিলন খুবই সম্ভবপর। বিয়ের পূর্বে স্বামী-স্ত্রী (বর-কনের) পরস্পরের সম্প্রীতি ও আন্তরিকতা সৃষ্টি হওয়ার আশা করা যায়, যা দাম্পত্য জীবনের স্থায়িত্বের জন্যে একান্তই অপরিহার্য।
হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেনঃ (আরবী****************)
আমি রাসূলে করীম (সা)-এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। এ সময় সেখানে এক ব্যক্তি এল। সে নবী করীম (সা)-কে আনসার বংশের একটি মহিলাকে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত করেছেন। তখন নবী করীম (সা) জিজ্ঞেস করলেনঃ তুমি কি তাকে দেখেছ? লোকটি বললঃ না। তখন নবী করীম (সা) জিজ্ঞেস করলেনঃ তুমি কি তাকে দেখেছ? লোকটি বললঃ না। তখন নবী করীম (সা) বললেনঃ এখনই যাও এবং তাকে দেখে নাও। কেননা আনসার বংশের মেয়েদের চোখে কিছু একটা (ত্রুটি) থাকে।
হযরত মুগীরা ইবনে শু’বা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি একটি মেয়েকে বিয়ের প্রস্তাব দিলেন। তখন নবী করীম (সা) বললেনঃ (আরবী****************)
তুমি আগে তাকে দেখ। কেননা এ বিয়ে-পূর্ব দর্শনে তোমাদের মধ্যে মিলমিশ স্থাপিত হওয়ার খুব বেশি সম্ভাবনা আছে। মুগীরা মেয়েটির পিতামাতার কাছে উপস্থিত হলেন এবং নবী করীম (সা) যা বলেছেন, তা তাদের জানিয়ে দিলেন। তারা ব্যাপারটিকে খুব ভাল মনে করল না। কিন্তু মেয়েটি নিজেই যখন পর্দার আড়াল থেকে এ কথা শুনতে পেল, তখন বলল, যদি রাসূলে করীম (সা)-ই দেখার জন্যে বলে থাকেন, তাহলে দেখে নিন। মুগীরা বললেনঃ মেয়েটির এ কথা শুনে আমি তাকে দেখলাম এবং তাকে বিয়ে করলাম। (আহমদ, ইবনে মাযাহ, তিরমিযী, দারেমী, ইবনে হাব্বান)
প্রস্তাবিত কনেকে কতটা দেখা যেতে পারে, নবী করীম (সা) সুস্পষ্ট ভাষায় তার কোন সীমা নির্দিষ্ট তার কোন সীমা নির্দিষ্ট করে দেননি। কিছু সংখ্যক বিশেষজ্ঞ বলেছেনঃ শুধু মুখমণ্ডল ও পাঞ্জাদ্বয় দেখা যেতে পারে। কিন্তু প্রস্তাবিত কনের ব্যাপারে তো এটা কোন বিশেষ ব্যবস্থা নয়, এটা তো অপ্রস্তাবিতা মহিলাকে দেখার ব্যাপারেও কার্যকর। বিয়ের পয়গাম না দেয়া হলেও তা দেখা জায়েয। বিয়ের পয়গাম দেয়া হলে সংশ্লিষ্ট মেয়েকে দেখার অনুমতিই প্রমাণ করে যে, সাধারণ অবস্থায় যতটা দেখা জায়েয, এ অবস্থায় তার চাইতে অনেক বেশি দেখার অনুমতি থাকা আবশ্যক এবং তা জায়েয হওয়া উচিত।
হাদীসে বলা হয়েছেঃ (আরবী****************)
তোমাদের কেউ যখন কোন মেয়েকে বিয়ের প্রস্তাব দেবে তখন সম্ভবপর হলে তার এমন কিছু অংশ তার দেখা উচিত, যা তাকে বিয়ে করতে উদ্বুদ্ধ করবে।
একদিকে কিছু বিশেষজ্ঞের মতে প্রস্তাবিতা কনেকে ভালভাবে দেখার অনুমতি আছে এবং অপরদিকে অপর কিছু আলিম এ ব্যাপারে খুব সংকীর্ণ দৃষ্টি রাখেন। এর মধ্যে মধ্যম মাত্রাই ভাল ও ভারসাম্যপূর্ণ। কিছু সংখ্যক বিশেষজ্ঞ এমত পোষণ করেন যে, বিয়ের প্রস্তাবদাতা পুরুষের পক্ষে প্রস্তাবিতা কনেকে দেখার এরূপ অনুমতি থাকা উচিত যে, মেয়ে যে পোশাকে তার বাপ-ভাই ও মুহাররম পুরুষদের সামনে আসা-যাওয়া করে, ঠিক সেই পোশাকেই তাকে দেখবে। শুধু তাই নয়, প্রস্তাবিতা কনের বুদ্ধি-বিবেচনা ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ গুণাবলীও পর্যবেক্ষণ বা পরীক্ষা করে দেখার জন্যে মেয়ের একজন মুহাররম পুরুষসহ তারা এমন এক স্থানে বসবে, যেখানে মেয়ে সাধারণত যাওয়া-আসা করে। তবে শর্ত এই যে, সেই স্থানটি বৈধ ধরনের হতে হবে এবং প্রস্তাবিতা কনে শরীয়তসম্মত পোশাক পরে থাকবে। এ মতের ভিত্তি হচ্ছে উপরিউক্ত হাদীসের অংশ, যাতে বলা হয়েছেঃ তার এমন কিছু অংশ দেখা উচিত যা তাকে বিয়ে করতে উদ্বুদ্ধ করবে। (আরবী****************)
প্রস্তাবদাতা পুরুষ প্রস্তাবিতা মেয়েকে তার এবং তার ঘরের লোকদের জানিয়ে রীতিমত আনুষ্ঠানিকভাবেও দেখতে পারে; আর কাউকে কিছু না জানিয়েও দেখতে পারে। তবে বিশেষ পয়গাম দেয়ার ও বিয়ে করার বাস্তব ও দৃঢ় সংকল্প থাকা অনিবার্য শর্ত বিশেষ। হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ তাঁর স্ত্রী সম্পর্কে বলেছেনঃ আমি তাকে দেখার জন্যে গাছের তলায় লুকিয়ে ছিলাম।
হযরত মুগীরা (রা) বর্ণিত উপরোদ্ধৃত হাদীস থেকে জানা গেল, কোন মুসলিম পিতামাতা যদি কোন রসম-রেওয়াজের নামে তাদের কন্যাকে দেখা থেকে এমন ব্যক্তিকে বাধা দেয় বা দেখাতে অস্বীকার করে, যে তাকে সত্যই বিয়ে করতে ইচ্ছুক, তাহলে সেসব রসম-রেওয়াজকে অবশ্যই শরীয়তসম্মত হতে হবে, তার বিপরীত নায়। শরীয়তকে রসম-রেওয়াজ বা প্রথা-প্রচলনের অধীন করে দেয়া তো শরীয়ত লংঘনের শামিল। কিন্তু দেখার এই অনুমতির সুযোগ পেয়ে কোন যুবক ছেলে কোন যুবতীর গলায় হাত দেবে, বিয়ের প্রস্তাবের দোহাই দিয়ে এক সঙ্গে থিয়েটার-সিনেমা, খেলার মাঠ বা হাটে-বাজারে চলে যাবে ও পরিভ্রমণ করবে এবং সঙ্গে কোন মুহাররম পুরুষ থাকবে না, তা করতে দেয়া মা-বাবার পক্ষে জায়েয নয়, প্রস্তাবদাতা পুরুষটির বা প্রস্তাবিতা কনের পক্ষেও এতটা উচ্ছৃঙ্খর হওয়া কোনক্রমেই জায়েয হতে পারে না। অথচ একালের পাশ্চাত্য সভ্যতার দাসানুদাসরা মেয়ে দেখার নাম করে এ সব করে বেড়াচ্ছে।
সত্যি কথা হচ্ছে, চরম পন্থা তা ডান দিকে হোক বা বাম দিকে, ইসলামী জীবন ব্যবস্থার সাথে তার কোন সামঞ্জস্যই নেই।
বিয়ের পয়গাম দেয়ার হারাম পন্থা
তালাকপ্রাপ্তা বা স্বামী-মরা স্ত্রীলোককে তার ইদ্দতের মধ্যে- ইদ্দত শেষ হওয়ার পূর্বেই-নতুন করে বিয়ের প্রস্তাব যে কোন মুসলমানের জন্যেই জায়েয নয়। কেননা ইদ্দতটা তো প্রাক্তন বিয়ের প্রতি সম্মান দেখানর উদ্দেশ্যে পালিত হয়ে থাকে। কাজেই এ ব্যাপারে কোনরূপ বাড়াবাড়ি করা কারো পক্ষেই জায়েয নয়। তবে স্বামী মরা স্ত্রীলোকটি ইদ্দত শেষে তার সাথে বিয়ে করতে আগ্রহী কিনা তা ইশারা-ইঙ্গিতে জানাবার জন্যে ইদ্দত পালনকালেই চেষ্টা করতে পারে কিন্তু প্রকাশ্যে ও স্পষ্ট ভাষায় নয়। আল্লাহ্ তা’আলা বলেছেনঃ (আরবী****************)
বিয়ের পয়গাম সম্পর্কে ইশারা-ইঙ্গিতে বলা হলে তাতে তোমাদের গুনাহ হবে না।
বিয়ের একটি প্রস্তাব সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার পূর্বেই তার ওপর আর একটি বিয়ের প্রস্তাব দেয়া জায়েয নয়- যদি প্রথম প্রস্তাবের কথাবার্তা সাফল্যের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। কেননা প্রথম প্রস্তাবদাতার প্রস্তাব সম্পর্কে একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হোক, এটা তার অধিকার। এ অধিকার অবশ্যই পূরণ হতে হবে। লোকদের পারস্পরিক সম্পর্ক রক্ষা ও অসৌজন্যমূলক আচরণ পরিহার করে চলার জন্যেই এরূপ করা জরুরী। অন্যথায়, প্রথম প্রস্তাবদাতার অধিকার হরণ করা হবে। আর তা নিশ্চয়ই বাড়াবাড়িমূলক কার্যক্রম। কিন্তু প্রথম প্রস্তাবদাতা নিজেই যদি ইচ্ছা ত্যাগ বা প্রস্তাব প্রত্যাহার করে নেয় অথবা নিজেই অপরকে প্রস্তাব দেয়ার অনুমতি দিয়ে দেয়, তাহলে দ্বিতীয় কারো পক্ষে প্রস্তাব দেয়ায় কোন দোষ নেই। রাসূলে করীম (সা) বলেছেনঃ (আরবী****************)
একজন মুমিন অপর মুমিনের ভাই। কাজেই অপর ভাইয়ের ক্রয়ের ওপর ক্রয় করা এবং অপর ভাইয়ের বিয়ের প্রস্তাবের ওপর প্রস্তাব পেশ করা জায়েয নয়।
নবী করীম (সা) আরও বলেছেনঃ (আরবী****************)
একজনের বিয়ের প্রস্তাব পরিত্যক্ত না হওয়া বা তার ওপর প্রস্তাব দেয়ার অনুমতি না দেয়ার পূর্বে অপর কারো প্রস্তাব দেয়া জায়েয নয়। (বুখারী)
কুমারী কন্যার অনুমতি, তার ওপর জোর না করা
যুবতী কুমারী কন্যা তার বিয়ের ব্যাপারে সর্বাধিক গুরুত্ব পাওয়ার অধিকারী। তার মতের প্রতি গুরুত্ব না দেয়া বা তার সম্মতি-অনুমতির প্রতি লক্ষ্য না রাখা তার পিতা বা অভিভাবকের জন্যে মোটেই জায়েয নয়। নবী করীম (সা) বলেনঃ (আরবী****************)
পূর্বে স্বামী পাওয়া মেয়ে তার নিজের ব্যাপারে তার অভিভাবকের অপেক্ষা বেশি অধিকার সম্পন্না। আর কুমারী কন্যার কাছ থেকে তার নিজের ব্যাপারে অবশ্যই অনুমতি নিতে হবে।
এক যুবতী মেয়ে নবী করীম (সা)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে জানাল যে, তার পিতা পিতার ভাইর পুত্রের সাথে তাকে বিয়ে দিয়েছে। কিন্তু এ বিয়ে তার পছন্দ নয়। তখন নবী করীম (সা) এ বিষয়ে ফয়সালা করার ইখতিয়ার তাকেই দিলেন। মেয়েটি বললঃ আমার পিতা যে আত্মীয়তা করেছে সে তা কার্যকর করেছে কিন্তু আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, আমি নারীকুলকে জানিয়ে দেব যেঃ (আরবী****************)
মেয়েদের ব্যাপারে বাপদের কিছু করার ইখতিয়ার নেই।
মেয়ের জন্যে দ্বীনদার চরিত্রবান সমমানের ছেলের কাছ থেকে বিয়ের প্রস্তাব এলে তার বিয়ে বিলম্বিত করার পিতার কোন অধিকার নেই। নবী করীম (সা) বলেছেনঃ (আরবী****************)
তিনটি ব্যাপার বিলম্বিত করা জায়েয নয়ঃ নামায- তার সময় হয়ে গেলে, জানাযা- লাশ উপস্থিত হলে এবং বিয়ে-যোগ্য মেয়ের বিয়ে- যদি সমান মানের প্রস্তাব পাওয়া যায়।
তিনি আরও বলেছেনঃ (আরবী****************)
যারা দ্বীনদারী ও চরিত্র তোমাদের পছন্দ মতো হবে, তার কাছে বিয়ে দাও। যদি তা না কর, তাহলে পৃথিবীতে চরম অশান্তি ও বিরাট বিপর্যয় দেখা দেবে।
মুহাররম মেয়েলোক
প্রত্যেক মুসলিম পুরুষের জন্যে নিম্নলিখিত মহিলাদের বিয়ে করা সম্পূর্ণ হারাম।
১. পিতার স্ত্রী- পিতার তালাক দেয়া স্ত্রী হোক কিংবা রেখে মরে গিয়ে থাক, উভয় অবস্থায় একই বিধান। ইসলামের পূর্ব জাহিলিয়াতের যুগে পিতার স্ত্রী বিয়ে করার প্রচলন ছিল। ইসলাম তাকে হারাম ঘোষণা করেছে। কেননা পিতার স্ত্রী তো মা সমতুল্য, পিতার সাথে তার একবার বিয়ে হয়ে যাওয়াই এ হারাম হওয়ার জন্যে যথেষ্ট। কেননা সন্তানের কাছে পিতার মর্যাদা অনেক বড় ও সম্ভ্রমপূর্ণ। পুত্রের জন্যে পিতার স্ত্রী চিরতরে হারাম হওয়ার কারণে তার প্রতি সন্তানের লোভ ও লালসা করাও চূড়ান্তভাবে হারাম হয়ে গেছে। ফলে পুত্র ও পিতার স্ত্রীর মধ্যে সম্মান ও মর্যাদার সম্পর্ক চিরদিনের জন্যে স্থায়ী ও অবিচল-অপরিবর্তিত হয়ে থাকল।
২. মা- গর্ভধারিণী, দাদী-নানীও অনুরূপভাবে হারাম।
৩. কন্যা- পুত্রের কন্যা ও মেয়ের কন্যাও এর মধ্যে শামিল, এভাবে এ তালিকা যতই লম্বা হোক না কেন।
৪. ভগ্নি- আপন হোক কিংবা মার দিক দিয়ে অথবা পিতার দিক দিয়েই হোক।
৫. ফুফু- পিতার বোন, আপন হোক কিংবা অন্য যে রকমই হোক।
৬. খালা- মা’র বোন
৭. ভাইয়ের কন্যা
৮. বোনের কন্যা
ইসলামে এ সব মহিলাদের ‘মাহারিম’ বা ‘মুহাররমাত’ বলে অভিহিত করা হয়েছে। কেননা মুসলিম ব্যক্তির জন্যে এরা চিরকালের তরে হারাম। কোন সময় এবং কোন অবস্থাতেই তারা হালাল নয়, এদের বিয়ে করা জায়েয নয়। এ সম্পর্কের দিক দিয়ে পুরুষটিকেও ‘মুহাররম’ বলা হয়।
এ সব মেয়ে বিয়ে করা হারাম হওয়ার কারণ
ক. সুসভ্য ও সুরুচিসম্পন্ন মানুষের প্রকৃতি স্বীয় মা-বোন-কন্যাকে স্বীয় যৌন লালসা চরিতার্থ করার জন্যে ব্যবহার করতে কখখনই রাজি বা প্রস্তুত হতে পারে না। মানুষ তো দূরের কথা, কোন-কোন পশুও তা করতে প্রস্তুত হয় না। খালা ও ফুফুর প্রতিও নিজের গর্ভধারিণী মার মতোই সম্ভ্রম বোধ থাকে, থাকে তেমনি শ্রদ্ধা-ভক্তি। অনুরূপভাবে চাচা এবং মামাও যে কোন নারীর জন্যে পিতার সমতুল্য শ্রদ্ধা-ভক্তিভাজন হয়ে থকে।
খ. ইসলামী শরীয়তে এসব ‘মুহাররমাত’ সম্পর্কে অনুরূপ সিদ্ধান্ত না দিলে তাদের প্রতি যৌন লালসাবোধকে চিরতরে হারাম করা না হলে এদের পরস্পরের মধ্যে যৌন সম্পর্ক গড়ে উঠা অসম্ভব ছিল না, কেননা এদের পরস্পরের মধ্যে নিভৃত একাকীত্বে খুব বেশি মেলামেশা হয়ে থাকে স্বাভাবিক পারিবারিক জীবন যাপনের কারণে।
গ. এসব নিকট-আত্মীয়তা সম্পন্ন লোকদের পরস্পরের মধ্যে গভীর আবেগপূর্ণ সম্পর্ক হয়ে থাকে, এ কারণে প্রতিটি মানুষ তাদের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধ করে। তাদের প্রতি গভীর-তীব্র সহানুভূতি ও হৃদয়াবেগ অনুভব করে। এ কারণে প্রেম-প্রীতি সহকারে এর বাইরের মহিলাদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনই বাঞ্ছনীয়। এতে করে নতুন আত্মীয়তার সূত্রে আপনজন, আত্মীয়-স্বজনের পরিধি সমাজের মধ্যে অনেক ব্যাপক ও সম্প্রসারিত হয়ে পড়ে এবং ভালবাসা ও সহানুভূতি সম্পর্কের ক্ষেত্রও বিস্তীর্ণ হয়ে যায়। কুরআনে সেদিকে ইঙ্গিত করেই বলা হয়েছেঃ (আরবী****************)
এবং তোমাদের মধ্যে বন্ধুতা ও ভালবাসার সম্পর্ক সৃষ্টি করে দিয়েছেন।
ঘ. এসব নিকটাত্মীয়তা সম্পন্ন লোকদের পরস্পরের মধ্যে যে স্বাভাবিক আবেগ রয়েছে, তা স্থায়ী হয়ে থাকা একান্তই জরুরী ও অপরিহার্য। তাদের মধ্যে যে স্থায়ী সম্পর্ক রয়েছে তা এ ভাবেই অটুট ও অক্ষয় হয়ে থাকেতে পারে, তা পরিপক্কতা লাভ করতে পারে। তাদের ভালবাসা ও পৃষ্ঠপোষকতা প্রভৃতির জন্যে সুদৃঢ় ভিত্তি রচিত হতে পারে। কিন্তু তার বিপরীত এদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার সুযোগ থাকলে এদের পরস্পরের মতদ্বৈততা হিংসা-বিদ্বেষ ও ঝগড়া-ফাসাদ হওয়া ছিল অবধারিত। আর তার ফলে পারিবারিক জীবনে আসত গভীর ভাঙন ও বিরাট বিপর্যয়। পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতা ও শত্রুতা এক অনিবার্য পরিণতি হয়ে দেখা দিত।
ঙ. এসব নিকটাত্মীয়তা সম্পন্ন নারী-পুরুষের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক হলে তাদের যে বংশ সৃষ্টি হতো তা সর্বদিক দিয়ে দুর্বল ও অকর্মণ্য হয়ে পড়া খুবই স্বাভাবিক। কোন পরিবারে দৈহিক বা বিবেক-বুদ্ধিগত কোন দুর্বলতা বা ত্রুটি থাকলে তা বংশানুক্রমে সংক্রমিত হয়ে সেই বংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে যেত।
চ. প্রত্যেক নারী তার পক্ষ সমর্থনকারী ও তার পক্ষে চেষ্টা-প্রচেষ্টাকারী পুরুষের মুখাপেক্ষী এবং তার ওপর অনেকটা নির্ভরশীল। তার স্বামীর সাথে সম্পর্কের অবনতি ঘটলে এরূপ ব্যক্তির অপরিহার্যতা তীব্র হয়ে উঠে। তখন স্বার্থরক্ষা ও তার পক্ষ সমর্থন করার জন্যে কেউ না থাকলে নারীর অসহায়ত্ব মর্মান্তিক হয়ে পড়ে। কিন্তু তার বিয়ে যদি এসব অতি আপনজনের মধ্যে কারো সাথে হয়ে যায়, তাহলে তার পক্ষে কথা বলার কোন লোক কোথাও পাওয়া যাবে না। কেননা তখন তার আপনজনই তার প্রতিদ্বন্দ্বী বা শত্রু হয়ে দাঁড়াবে।
দুগ্ধ সেবনের কারণে বিয়ে হারাম হওয়া
৯. শৈশবকালে যে পুরুষ ছেলে যে নারীর বুকের স্তন পান করেছে তার পক্ষে এ নারীকে বিয়ে করা সম্পূর্ণ হারাম। কেননা এ দুগ্ধ পান করানর কারণে সে তো তার মা সমতুল্য হয়ে গেল। তার দেহে যে মাংসপেশী ও অস্থিমজ্জা গড়ে উঠেছে তাতে তার বুকের দুগ্ধ গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ দুগ্ধ পানের দরুন দুজনের মধ্যে মা-সন্তানের এক নতুন আবেগপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। একথা সত্য যে, অনেক সময় এ সম্পর্ক প্রচ্ছন্ন হয়ে থাকে। কিন্তু ব্যক্তি অবচেতনায় তা বহুদিন পর্যন্ত বর্তমান থাকে এবং প্রয়োজনের সময় তা প্রকট হয়ে দেখা দেয়া।
দুগ্ধ পানের দরুন শরীয়তের এ বিধান কার্যকর হবে যদি তা শৈশব কালে অর্থাৎ দুই বছর বয়স পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই- পান করা হয়। কেননা এ বয়সেই নারীর বুকের দুগ্ধ সেবন করে থাকে, তবেই শরীয়তের হুকুম কার্যকর হবে। আর তার লক্ষণ হচ্ছে এই যে, শিশুটি দুগ্ধ সেবন করতে করতে পেট ভরে যাওয়ার দরুন নিজেই পান করা ছেড়ে দেবে, স্তনের বোটা শিশুর মুখ থেকে আপনা-আপনি খসে পড়বে।
এ পাঁচবার পানের শর্তটি হাদীসের বিভিন্ন বর্ণনার ভিত্তিতে অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য।
১০. দুধ-বোন বিয়ে করাও হারাম। নারী যেমন পুরুষ ছেলের দুধ-মা হয়, তেমনি সেই নারীর গর্ভজাত কন্যারাও তার দুধ-বোন হবে। এ নারীর বোনেরা হবে তার দুধ খালা। অপরাপর আত্মীয়রাও তার দুধ সম্পর্কের দিক দিয়ে আত্মীয় হয়ে যাবে।
এ পর্যায়ে নবী করীম (সা)-এর হাদীস হচ্ছেঃ (আরবী****************)
বংশ সম্পর্কের দরুন যা যা হারাম, দুধ সম্পর্কের কারণেও তা তা-ই হারাম হয়ে যাবে।
বংশের আত্মীয়তার কারণে যেমন ফুফু, খালা, ভাইঝি ও ভাগ্নী বিয়ে করা হরাম, দুধ-পানের দরুনও সেই সব আত্মীয়ের সাথে বিয়ে সম্বন্ধ হারাম হয়ে যাবে।
বৈবাহিক সম্পর্কের দরুন বিয়ে হারাম
১১. স্ত্রীর মা- অর্থাৎ শাশুড়ী। তাকে বিয়ে করাও হারাম। কোন নারীর কন্যা বিয়ে করলেই সেই নারী তার জন্যে হারাম হয়ে যাবে- সে কন্যার সাথে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক কার্যকর হোক আর নাই হোক, কেননা শাশুড়ি মা’র সমান।
১২. পালিতা কন্যা- অর্থাৎ যে স্ত্রীর সাথে স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক কার্যকর হয়েছে, তার কন্যা স্বামীর জন্যে হারাম। যদি সে সম্পর্ক বাস্তবভাবে কার্যকর না হয়ে থাকে, তাহলে তার কন্যা বিয়ে করায় কোন দোষ নেই।
১৩. স্বীয় ঔরসজাত পুত্রের স্ত্রী। পালিত পুত্রের স্ত্রী হারাম নয়। কেননা ইসলামে কোন ছেলেকে লালন-পালন করলেও সে আপন ঔরসজাত ছেলে হয়ে যায় না। জাহিলিয়াতের যুগে এ ব্যবস্থা কার্যকর ছিল, কিন্তু ইসলাম তা বাতিল করে দিয়েছে। কেননা তাতে বাস্তব ও প্রকৃত অবস্থাকে অস্বীকার করা হয়। তাতে হালালকে হারাম ও হারামকে হালাল গণ্য করা হয়। আল্লাহ্ তা’আলা বলেছেনঃ (আরবী****************)
তোমাদের মুখ ডাকা পুত্রকে প্রকৃত পুত্র বানিয়ে দেয়া হয়নি। কেননা তাতো শুধু তোমাদের মুখের কথা মাত্র। (সূরা আহযাবঃ ৪)
আর শুধু মুখের কথায় প্রকৃত ও বাস্তব কখনও পরিবর্তিত হয়ে যায় না। পর আপন হয়ে যায় না।
এ তিনজনের সাথে বিয়ের সম্পর্ক স্থাপন হারাম বৈবাহিকতার কারণে। বৈবাহিকতার দরুন যে আত্মীয়তা গড়ে উঠে, তাতে এ বিবাহ হারাম হওয়া একান্তই বাঞ্ছনীয়।
দুই বোনককে এক সঙ্গে স্ত্রী বানান
১৪. দুই বোনকে একসঙ্গে স্ত্রীরূপে গ্রহণ হারাম। জাহিলিয়াতের যুগে এরূপ করার ব্যাপক প্রচলন ছিল। কিন্তু ইসলাম তা হারাম করে দিয়েছে। তার কারণ, দুই বোনের পারস্পরিক আপনত্বের সম্পর্ক এরূপ অবস্থায় টিকে থাকতে পারে না। অথচ ইসলামের লক্ষ্য হচ্ছে এ সম্পর্ককে অটুট ও অপরিবর্তিত রাখা। কিন্তু দুই বোন যখন সতীন হয়ে দাঁড়াবে, তখন এই সম্পর্ক শেষ হয়ে যাবে, দু’জন দু’জনার শত্রুতে পরিণত হবে অতি স্বাভাবিকভাবেই।
কুরআন মজীদে দুই বোনকে এক সঙ্গে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করাকে স্পষ্ট ভাষায় হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। রাসূলে করীম (সা) অতিরিক্ত এই নির্দেশ দিয়েছেনঃ (আরবী****************)
একটি মেয়ে ও তার ফুফু এবং একটি মেয়ে ও তার খালাকে এক সঙ্গে স্ত্রী বানান যাবে না।
তিনি আরও বলেছেনঃ (আরবী****************)
তোমরা যদি এরূপ কাজ কর তাহলে তোমরা নিকটাত্মীয়তার সম্পর্ককে ছিন্ন করার অপরাধ করবে।
অথচ ইসলাম এই নিকটাত্মীয়তার সম্পর্ক (আরবী****************) কে অটুটু রাখতে বদ্ধপরিকর। তাহলে তাতে এমন কাজ কি করে জায়েয হতে পারে, যা এই পরিণতির সৃষ্টি করে?
পরস্ত্রী
১৫. যেসব মেয়ে কোন পুরুষের স্ত্রী হয়ে আছে এই অবস্থায় অপর কোন স্বামী গ্রহণ করা তাদের জন্যে সম্পূর্ণ হারাম।
এরূপ একজন স্ত্রীলোককে অন্য কোন পুরুষের পক্ষে বিয়ে করা জায়েয হতে পারে কেবলমাত্র দুটি অবস্থায়ঃ
ক. তার বর্তমান স্বামী হয় মরে যাবে কিংবা তালাক দেবে এবং এভাবে তার স্বামীত্ব অপমৃত্যু ও নিঃশেষ হয়ে যাবে।
খ. অতঃপর স্ত্রীলোকটির জন্যে আল্লাহ্ তা’আলা যে ইদ্দতের মেয়াদ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, তা পূর্ণ হবে এবং পূর্ববর্তী স্বামীর প্রতি তার কর্তব্য পালিত হয়ে যাবে, তার জন্যে সংরক্ষণের ব্যবস্থা কায়েম হবে। স্ত্রীলোক গর্ভবতী হলে তার সন্তা প্রসবেই এই মেয়াদ সমাপ্ত হয়ে যাবে। সেই মেয়াদ সংক্ষিপ্ত হোক কি দীর্ঘ।
যে স্ত্রীর স্বামী মরে গেছে, তার জন্যে ইদ্দতের এ মেয়াদ হচ্ছে চার মাস দশ দিন।
আর তালাক প্রাপ্তা হলে তার ইদ্দতের মেয়াদ তিন হায়েয। তার গর্ভে কোন সন্তান নেই সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার জন্যে এ মেয়াদ একান্তই জরুরী। কেননা প্রাক্তন স্বামীর কাছ থেকে তার গর্ভে সন্তান থাকার আশংকা তো রয়েছেই। কাজেই দুই ধারার বংশের সংমিশ্রণ বন্ধের জন্যে এ ইদ্দত পালন অপরিহার্য। তবে স্ত্রী যদি অল্প বয়স্কা বা হায়েয বন্ধ হয়ে যাওয়া বৃদ্ধা হয়, তাহলে তাদের ইদ্দত হচ্ছে মাত্র তিন মাস। আল্লহ্ তা’আলা ইরশাদ করেছেনঃ (আরবী****************)
তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীরা তিন হায়েয শুকিয়ে যাওয়ার মেয়াদ পর্যন্ত নিজেদের বিরত রাখবে। তাদের গর্ভে আল্লাহ্ যা সৃষ্টি করেছেন তাকে গোপন করা তাদের জন্যে জায়েয নয় যদি তারা আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি ঈমানদার হয়ে থাকে। (সূরা বাকারাঃ ২২৮)
বলেছেনঃ (আরবী****************)
তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যাদের হায়েয হওয়ার আশা নেই তাদের সম্পর্কে তোমাদের মনে সন্দেহ হলে তারা তিন মাস পর্যন্ত ইদ্দত পালন করবে। তাদেরও ইদ্দত এ মেয়াদ যাদের হায়েয বন্ধ হয়েছে এবং গর্ভবতী স্ত্রীদের ইদ্দত হচ্ছে গর্ভ প্রসব।
আরও বলেছেনঃ (আরবী****************)
তোমাদের মধ্য থেকে যারা মরে যায় ও স্ত্রী রেখে যায়, সেই স্ত্রীরা চার মাস দশদিন ইদ্দত পালনে রত থাকবে। (সূরা বাকারাঃ ২৩৪)
উপরিউল্লিখিত পনের প্রকারের নারীদের বিয়ে করা ইসলামে হারাম। কুরআন মজীদের সূরা আন-নিসা’র তিনটি আয়াতে তা একসঙ্গে ঘোষণা করা হয়েছে। সেই আয়াত তিনটি এইঃ (আরবী****************)
তোমাদের পিতা যে মেয়েলোক বিয়ে করেছে, তোমরা তাদের বিয়ে করো না। তার পূর্বে যা হয়ে গেছে, (তা বাদে) এটা সুস্পষ্ট নির্লজ্জতা, অত্যন্ত পাপ ও খুবই খারাপ পন্থা, সন্দেহ নেই। তোমাদের প্রতি হারাম করা হয়েছে, তোমাদের মা’দের। তোমাদের কন্যাদের, বোনদের, তোমাদের ফুফুদের, তোমাদের খালাদের, তোমাদের ভাইঝিদের, তোমাদের ভাগ্নীদের এবং তোমাদের সেসব মা, যারা তোমাদের দুধ পান করিয়েছে, আর তোমাদের দুধ-বোনদের এবং তোমাদের স্ত্রীদের মা’দের (শাশুড়ীদের),আর তোমাদের স্ত্রীদের কন্যাদের, যারা তোমাদের স্ত্রীদের কোলে লালিত এবং তোমাদের সে সব স্ত্রীদের গর্ভজাত যাদের সাথে তোমাদের স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। যদি স্বামী-সম্পর্ক স্থাপিত না হয়ে থাকে, তাহলে তাদের কন্যাদের বিয়ে করায় কোন দোষ হবে না এবং তোমাদের ঔরসজাত পুত্রদের স্ত্রীদের। আর তোমাদের দুই বোনকে এক সঙ্গে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করবে (তা-ও নিষিদ্ধ) তবে পূর্বে যা হয়ে গেছে, তার কথা নয়। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়াবান। সে সব স্ত্রীলোকও হারাম যারা বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ রয়েছে.........। (সূরা আন-নিসাঃ ২২-২৪)
মুশরিক নারী
১৬. মুশরিক নারী বিয়ে করাও হারাম। আর মুশরিক নারী তারা যারা মূর্তি পূজা করে। প্রাচীন আরব ও ভারতীয় হিন্দু মুশরিকগণ এ পর্যায়ে গণ্য।
আল্লাহ্ তা’আলা স্পষ্ট ভাষায় বলেছেনঃ (আরবী****************)
মুশরিক নারী তাওহীদী ঈমান গ্রহণ না করা পর্যন্ত তাদের বিয়ে করবে না। জেনে রাখ, ঈমানদার দাসীও মুশরিক নারীর তুলনায় অনেক ভাল, সে তোমার যতই পছন্দ ও মনলোভা হোক। তোমরা মুশরিকদের কাছে নিজেদের মেয়ে বিয়ে দেবে না, যতক্ষণ না তারা ঈমান আনবে। কেননা একজন ঈমানদার দাসও মুশরিকের তুলনায় অনেক ভাল, সে তোমাদের যতই পছন্দ হোক। ওরা জাহান্নামের দিকে ডাকে আর আল্লাহ্ জান্নাত ও ক্ষমার দিকে ডাকেন তাঁর অনুমতিক্রমে।
এ আয়াত স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছে যে, কোন মুসলমানের পক্ষে মুশরিক নারী বিয়ে করা জায়েয নয়। মুসলিম নারীর পক্ষেও জায়েয নয় মুশরিক পুরুষ বিয়ে করা। কেননা তাওহীদী দ্বীন ও মুশরিকী ধর্মের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান। ঈমানদার লোক তো জান্নাতের দিকে মানুষকে নিয়ে যায় আর মুশরিকরা নিয়ে যায় জাহান্নামে। ওরা ঈমানদার এক আল্লাহ্, রাসূল, নবুওয়্যত, পরকালের প্রতি। আর এরা আল্লাহর সঙ্গে শিরক করে, নবুওয়্যত অস্বীকার করে এবং পরকালকে করে অবিশ্বাস।
অথচ বিয়ে হচ্ছে মনের শান্তি, স্থিতি ও বন্ধুতা সম্প্রীতির ব্যাপার। কাজেই তাতে এ দুটি পরস্পর বিরোধী ভাবধারা একত্র সমাবেশ অসম্ভব।
আহলি কিতাব নারী
কুরআন মজীদ ইয়াহূদ ও খ্রিস্টান এই দুই আহলি কিতাব সম্প্রদায়ের মেয়ে বিয়ে করার অনুমতি মুসলমানকে দিয়েছে। তাদের সাথে বিশেষ আচরণ গ্রহণ করারও নির্দেশ রয়েছে। তারা যদিও নিজেদের দ্বীনের অনেক কিছুই রদ-বদল করে ফেলেছে, তবুও তারা যে আসমানী দ্বীনের অনুসারী তা অবশ্যই মানতে হবে। তাই তাদের যবাই করা জন্তু খাওয়া যেমন মুবাহ করেছে তেমনি তাদের মেয়ে বিয়ে করাও জায়েয় ঘোষণা করছে। আল্লাহ্ তা’আলা ইরশাদ করেছেনঃ (আরবী****************)
আহলি কিতাবের খাদ্য তোমাদের জন্যে হালাল, তোমাদের খাদ্য তাদের জন্যে হালাল। আর পবিত্র চরিত্র ও সতীত্ব সম্পন্ন মুমিন স্ত্রীলোক এবং তোমাদের পূর্বে কিতাব পাওয়া পবিত্র চরিত্র ও সতীত্ব সম্পন্ন স্ত্রী লোকও যদি তোমরা তাদের মোহরানা আদায় করে দাও, পবিত্রতা রক্ষাকারী হিসেবে, জ্বেনাকার হিসেবে নয় এবং বন্ধুতার সূত্র গ্রহণকারী হিসেবেও নয়।
অবশ্য এটা ইসলামের উদার নীতিসমূহের মধ্যে একটা বিশেষ দিক। দুনিয়ার অন্যান্য জাতি ও ধর্মসমূহে এর দৃষ্টান্ত খুব কমই পাওয়া যায়। এসব আহলি কিতাবকে কুফর ও গুমরাহ বলা সত্বেও এসব ধর্মাবলম্বী নারী নিজ নিজ ধর্মে অবিচল থেকেও মুসলমানের স্ত্রী ও তার ঘরের রানী হতে পারে বলে ইসলাম ঘোষণা করেছে। তারা হতে পারে মুসলিম ব্যক্তির মনের সান্ত্বনা, তার গোপনীতার সাক্ষী এবং তার সন্তানের মা। ইসলাম তার অনুমতি দিয়েছে, এমতাবস্থায়ও যখন ইসলামে স্ত্রীত্বের সম্পর্ক ও তার গোপন তত্ত্ব পর্যায়ে কুরআন বলেছেঃ (আরবী****************)
আল্লাহর একটি নিদর্শন হচ্ছে, তিনি তোমাদের জন্যে তোমাদেরই মধ্যে স্ত্রী বানিয়ে দিয়েছেন, যেন তোমরা তাদের কাছে সান্ত্বনা লাভ করতে পার এবং তোমাদের মধ্যে বন্ধুতা-ভালবাসা ও দয়া-সহানুভূতি সৃষ্টি করেছেন।
এ পর্যায়ে একটি বিষয়ে সতর্ক করে দেয়া একান্তই অপরিহর্য। একজন দ্বীনদার- দ্বীনের প্রতি ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও আকর্ষণ সম্পন্ন মুসলিম সহিলা কেবলমাত্র বংশানুক্রমিক মুসলিম মহিলার তুলনায় অনেক উত্তম। রাসূলে করীম (সা) আমাদের এ কথা শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি বলেছেনঃ (আরবী****************)
দ্বীনদার নারীকে বিয়ে কর, সেই তোমার সাফল্যের কারণ হবে। (তা না করা হলে) তোমাদের হাত মাটি-মিশ্রিত হোক।
এ থেকে জানা গেল যে, যে কোন আহলি কিতাব নারীর তুলনায় যে কোন মুসলিম নারী মুসলিম পুরুষের জন্যে স্ত্রীরূপে উত্তম হতে পারে।
তাছাড়া এ ধরনের স্ত্রী গ্রহণ করা হলে তার সন্তানের ওপর তার আকীদা-বিশ্বাসের প্রভাব পড়বে এবং তাদেরও বিভ্রান্ত করবে- এ আশাংকা যখন তীব্র ও নিশ্চিত, তখন দ্বীন রক্ষার উদ্দেশ্যেই এসব আশংকা থেকে রক্ষা পাওয়া ও এ ধরনের স্ত্রী গ্রহণ না করাই বাঞ্ছনীয়।
এতদ্ব্যতীত কোন দেশে যদি মুসলমানদের সংখ্যা কম থাকে, তাহলে, এরূপ অবস্থায় মুসলিম পুরুষদের আহলি কিতাব স্ত্রী গ্রহণ সম্পূর্ণ হারাম হওয়া উচিত। কেননা তখন মুসলিম পুরুষরা যদি মুসলিম মেয়েদের বাদ দিয়ে আহলি কিতাব মেয়ে বিয়ে করে, তাহলে মুসলিম নারীদের বিয়ে হওয়া সম্ভব হবে না এবং তার ফলে তারা চরমভাবে দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়বে। কেননা তাদের বিয়ে তো অমুসলিম পুরুষদের সাথে হতে পারে না, তা জায়েয নয় বলে। তখন ওদের কেউ বিয়ে করার থাকবে না। এরূপ অবস্থা মুসলিম সমাজের পক্ষে খুবই মারাত্মক হয়ে দেখা দেবে। তাই আহলি কিতাব মেয়ে বিয়ে করা মুসলিম পুরুষের জন্যে জায়েয হলেও এরূপ অবস্থায় তার অবকাশ না রাখাই উক্ত বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার একমাত্র উপায় বলে বিবেচিত।
অমুসলিম পুরুষের সাথে মুসলিম নারীর বিয়ে
মুসলিম নারীকে অমুসলিম পুরুষের কাছে বিয়ে দেয়া সম্পূর্ণ রূপে হারাম, সে অমুসলিম আহলি কিতাব হোক কি অন্য কেউ। মুসলিম নারীর জন্যে তা কোন অবস্থায়ই জায়েয নয়। এ পর্যায়ে কুরআনী হুকুম পূর্বেও উদ্ধৃত হয়েছে। হুকুমটি এইঃ (আরবী****************)
তোমরা তোমাদের মেয়ে মুশরিকদের কাছে বিয়ে দেবে না, যতক্ষণ না তারা ঈমান গ্রহণ করবে।
হিজরত করে আসা মুমিন নারীদের সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ (আরবী****************)
হিজরত করে আসা মহিলাদের তোমরা যদি মুমিন বলে জান, তাহলে তাদের কাফিরদের কাছে ফেরত পাঠিয়ে দিও না। কেননা এরা তাদের জন্যে হালাল নয়, তারাও হালাল নয় এদের জন্যে।
এখানে আহলি কিতাবদের বাদ দিয়ে একথা বলা হয়নি। কাজেই মুসলিম মহিলাদের কাফির মুশরিক-অমুসলিম পুরুষদের কাছে বিয়ে দেয়া হারাম হওয়ার ব্যাপারে কোন ভিন্নমতের অবকাশ নেই।
ইসলামে ইয়াহূদী-খ্রিস্টান মেয়ে বিয়ে করা জায়েয করা হয়েছে, কিন্তু মুসলিম নারীকে তাদের কাছে বিয়ে দেয়া হারাম করা হয়েছে, তার মূলে যুক্তি সঙ্গত কারণ রয়েছে। কেননা পুরুষই হয় ঘরের পরিবারের কর্তা ও নারীর ওপর কর্তৃত্বসম্পন্ন। সে-ই সব বিষয়ে প্রত্যক্ষভাবে দায়ী। উপরন্তু ইসলাম আহলি কিতাব স্ত্রীকে তার আকীদা-বিশ্বাসের পূর্ণ স্বাধীনতার অধিকার দিয়েছে। শরীয়তের আইন বিধানের সাহায্যে তার অধিকার সম্পর্কের সংরক্ষণও করেছে। তার মান-মর্যাদা রক্ষারও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। কিন্তু ইয়াহূদী খ্রিস্টান (বা হিন্দু) ধর্ম অপর কোন ধর্মাবলম্বী স্ত্রীর কোনরূপ অধিকার মর্যাদা বা স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দেয়নি। তার অধিকার রক্ষা করা হবে বলে কোন প্রতিশ্রুতিও পাওয়া যায় নি। এরূপ অবস্থায় ইসলাম কোন মুসলিম নারীকে অমুসলিম পুরুষের কাছে বিয়ে দেয়ার অনুমতি দিয়ে তাকে এই কঠিন বিপদে কি করে ঠেলে দিতে পারে? এই মুসলিম নারীর দ্বীনী আকীদা ও চরিত্র সংরক্ষণে নিশ্চয়তা দেয় না এমন পুরুষের কাছে তাদের সমর্পণ করার নীতি গ্রহণ করা- কিছুতেই সম্ভবপর নয়।
মূলত স্বামীর উচিত স্ত্রীর ধর্ম বিশ্বাস ও চরিত্রকে সম্মান ও মর্যাদা দেয়া। দুজনের মধ্যে উত্তম সম্পর্ক এরূপ করা হলেই রক্ষা পেতে পারে। মুসলমানরা তো ইয়াহূদী খ্রিস্টানদের- তাদের আকীদা-বিশ্বাসের অনেক মৌলিক পরিবর্তন সাধিত হওয়া সত্ত্বেও আসমনী ধর্মে বিশ্বাসী বলে মনে করে। তওরাত ও ইনজীল আল্লাহর কিতাব বলে মানে। হযরত মূসা ও ঈসা (আ) আল্লাহর মহান নবী ও রাসূল ছিলেন বলেও বিশ্বাস করে। এ কারণে কোন আহলি কিতাব নারীর পক্ষে একজন মুসলিমের স্ত্রী হয়ে স্বধর্মে স্থিত হয়ে জীবন যাপন করা ও শান্তি-সুখে থাকা খুবই সম্ভবপর। কেননা সেই স্বামী তো তার (স্ত্রীর) আমলম দ্বীন, কিতাব ও নবীকে মান্য করে। শুধু তাই নয়, তাকে সত্য সঠিক না মানলে মুসলিমানের ঈমানই শুদ্ধ ও সঠিক হয় না বলেও সে জানে। কিন্তু ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানদের আচরণ সম্পূর্ণ বিপরীত। তারা ইসলামকে আদৌ স্বীকৃতি দেয় না। ইসলামের কিতাব এবং তার রাসূলকেও তারা মানে না। তাহলে একচন ইসলামে বিশ্বাসী নারী কি করে এরূপ স্বামীর স্ত্রীত্বে সুখে-শান্তিতে জীবন যাপন করতে পারে? কেননা সে তো দ্বীন ও ইসলামী ইবাদত-বন্দেগী পালন করবে এবং ইসলামের মান-মর্যাদা, তার রীতি-নীতির বাস্তবতা রক্ষা করতে চেষ্টিত হবে। শরীয়তের হারাম থেকে নিজেকে রক্ষা করবে এবং কর্তব্যগুলো পালন করবে। কিন্তু এরূপ স্বামীর অধীন থেকে তা কার্যত সম্ভবপর হবে না। কেননা তাকে তো তার অমুসলিম স্বামীর কর্তৃত্ব মেনে চলতে হবে।
এ আলোকেই মুসলিম পুরুষের জন্যে মূর্তি পূজারী মুশরিক নারী বিয়ে করাকে ইসলামে হারাম ঘোষণা করার যৌক্তিকতা বুঝতে পারা যায়। কেননা ইসলাম শিরক ও মূর্তি পূজার সম্পূর্ণ বিরোধী, তা পূর্ণমাত্রায় অস্বীকারকারী। ফলে এ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কাম্য পরম প্রীতি ও বন্ধুতা ভালবাসা গড়ে উঠা ও স্থায়ী হওয়া সম্ভব নয়।
ব্যভিচারে অভ্যস্ত নারী
ব্যভিচারে অভ্যস্থ ও বেশ্যাবৃত্তিতে লিপ্ত ও প্রকাশ্যভাবে এ পেশা অবলম্বনকারী নারী বিয়ে করা কোন ঈমানদর মুসলমানের জন্যে জায়েয নয়। হযরত মুরসাদ ইবনে আবুল মুরসাদ (রা) নবী করীম (সা)-এর কাছে এমন একটি বেশ্যাকে বিয়ে করার অনুমতি চেয়েছিলেন যার সাথে জাহিলিয়াতের যুগে তাঁর সম্পর্ক ছিল। এ মেয়েটির নাম ছিল ‘ইনাক’। এ কথা শুনে নবী করীম (সা) তাঁর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। এ সময় কুরআনের আয়াত নাযিল হলঃ (আরবী****************)
ব্যভিচারকারী পুরুষ ব্যভিচারকারী বা মুশরিক নারী ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করবে না এবং ব্যভিচারী নারীকে ব্যভিচারকারী বা মুশরিক পুরুষ ছাড়া আর কেউ বিয়ে করবে না, ঈমানদার লোকদের জন্যে এরা হারাম।
নবী করীম (সা) সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে আয়াতটি পাঠ করে শোনালেন এবং তাঁকে বললেনঃ (আরবী****************) না, তুমি তাকে বিয়ে করবে না।
তার কারণ হচ্ছে, আল্লাহ্ তা’আলা ঈমানদার পুরুষদের জন্যে ঈমানদার সচ্চরিত্র সম্পন্ন নারীদের এবং আহলি কিতাব সমাজের অনুরূপ ধরনের মেয়েদের বিয়ে করা জায়েয করে দিয়েছেন। আর তা জায়েয করা হয়েছে এই শর্তে যে, তাঁরা (আরবী****************) বিয়ে বন্ধনে গ্রহণকারী হবে জ্বেনাকারী হবে না।
কাজেই যে লোক আল্লাহর কিতাবের এ নির্দেশ অমান্য করবে, তা পালন করতে প্রস্তুত হবে না, সে তো মুশরিক। তাকে বিয়ে করতে তারই মতো আর একজন মুশরিক পুরুষই রাজি হতে পারে, কোন মুমিন তা পারে না। আর যে ব্যক্তি এ হুকুম মানল, কবুল করল, কিন্তু তা সত্ত্বেও তার বিপরীত আমল করতে গিয়ে যে বিয়ে হারাম করা হয়েছে, তা করতে প্রস্তুত হলো, সে তো ব্যভিচারী হয়ে গেল।
সূরা নূর-এর উপরিউক্ত আয়াতটি উক্ত সূরার অপর একটি আয়াতের পরে উদ্ধৃত হয়েছে। সে পূর্ববর্তী আয়াতটিতে ব্যভিচারের দণ্ডের উল্লেখ করে বলা হয়েছেঃ (আরবী****************)
ব্যভিচারকারী নারী ও পুরুষ উভয়কেই এবং প্রত্যেককেই একটি করে চাবুক মার।
এ হচ্ছে ব্যভিচারের দৈহিক দণ্ড। আর উপরে যা বলা হয়েছে তা হচ্ছে ব্যভিচারের নৈতিক ও প্রশিক্ষণমূরক দণ্ড। কেননা ব্যভিচারী নারী বা পুরুষ বিয়ে করা হারাম করে দেয়ার মূল লক্ষ্যই হচ্ছে তাদের গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদাসম্পন্ন স্থানে অবস্থান করতে না দেয়া, তার জাতীয়তা অস্বীকার করা। আর বর্তমান প্রচলিত কথানুযায়ী তার অধিকারসমূহ হরণ করা- তা থেকে তাকে বঞ্চিত রাখা।
ইমাম ইবনুল কাইয়্যেম পূর্বোক্ত আয়াতটির ব্যাখ্যাদানের পর লিখেছেনঃ
কুরআনের এ হুকুমটি যেমন সুম্পষ্ট ও অবশ্য পালনীয়, তেমনি তা বিবেক-বুদ্ধি ও প্রকৃতিসম্মতও। আল্লাহ্ তা’আলা তাঁর বান্দাদের জন্যে কোন চরিত্রহীন নারীর স্বামী, দয়ূস বা বন্ধু-সঙ্গী হতে সম্পূর্ণ হারাম করে দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা’আলা মানুষকে যে প্রকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন, তা-ই এরূপ কাজকে অত্যন্ত জঘন্য, দোষযুক্ত ও বীভৎস জ্ঞান করে। এ কারণেই কোন ব্যক্তিকে খুব বেশি গাল-মন্দ করতে হলে বলা হয়ঃ ‘ফাহেশা স্ত্রীর স্বামী’। এ জন্যে বাস্তবিকই এরূপ হওয়া মুসলমানের জন্যে আল্লাহ্ তা’আলা হারাম করে দিয়েছেন। এ হারাম ঘোষণায় এ কথাও স্পষ্ট হয়ে গেল যে, স্ত্রীর এ পাপ স্বামীর শয্যা ও বংশকেও চরমভাবে বিপর্যস্ত করে দেবে অথচ আল্লাহ্ তা’আলা বংশধারা পরম পবিত্র ও কল্যাণময় ভিত্তির ওপর সংস্থাপিত করতে চান। এটাকে তাঁর একটি বিশেষ নিয়ম বলেও ঘোষণা করেছেন। কিন্তু জ্বেনা শুক্রকীটের সংমিশ্রণের পথ করে দেয়, বংশ সন্দেহপূর্ণ হয়ে যায়। এ জন্যে শরীয়তের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তা ব্যভিচারী নারীকে বিয়ে করা হারাম করে দিয়েছে। তবে তওবা করলে ও নিজের গর্ভধারা পবিত্র করে নিলে (অনন্ত এক হায়েয কাল অপেক্ষা করলে) ভিন্ন কথা (অর্থাৎ তখন বিয়ে করা জায়েয)। (আরবী****************)
ব্যভিচারিণীকে বিয়ে করা হারাম হওয়ার আর একটি কারণ হচ্ছে, ব্যভিচারী নারী অত্যন্ত ‘খবীস’ হয়ে থাকে। অথচ আল্লাহ্ তা’আলা বিষয়টিকে একটা বন্ধুতা-ভালবাসা-সম্প্রীতির পবিত্র বন্ধন বানিয়েছেন। বন্ধুতা প্রকৃত ভালবাসা। কোন ‘খবীস’ মেয়ে পবিত্র চরিত্রের পুরুষের প্রিয়তমা স্ত্রী হতে পারে না। স্বামীকে আরবী ভাষায় বলা হয় (আরবী****************) ‘যাওজুন’। এ শব্দটি (আরবী****************) ‘ইযদিওয়াজ’ থেকে নির্গত। আর তার অর্থ সাদৃশ্য সামঞ্জস্য সম্পন্ন হয়ে থাকে সর্বদিক দিয়ে। কিন্তু ‘খবীস’ এ ‘পবিত্র’ এ দুয়ের মাঝে পূর্ণ মাত্রায় ঘৃণ্য ও বিতৃষ্ণার ভাব প্রকট হয়ে থাকে অবধারিত। শরীয়তের দৃষ্টিতে, সাধারণ মূল্যবোধের বিচারেও, ফলে এ দুজনের মধ্যে কাম্য পারস্পরিক আন্তরিকতা ও সুগভীর প্রেম প্রণয়ন ভালবাসা ও মিলমিশ হওয়া সম্ভব নয়। তাই আল্লাহ্ তা’আলা সত্যই বলেছেনঃ (আরবী****************)
খবীস নারী খবীস পুরুষদের জন্যে এবং খবীস পুরুষ খবীস নারীদের জন্যে। আর পবিত্র চরিত্রা নারী পবিত্র চরিত্র পুরুষদের জন্যে এবং পবিত্র চরিত্র পুরুষ পবিত্র চরিত্রা নারীদের জন্যে। (সূরা নূরঃ ২৬)
সাময়িক বিয়ে
ইসলামে বিয়ে একটি সুদৃঢ় বন্ধন; একটি দুরতিক্রম্য প্রতিশ্রুতি। উভয় পক্ষ থেকে চিরদিনের একত্র জীবন যাপনের অপরিসীম আগ্রহ ও উৎসাহের ফলশ্রুতি। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মানসিক প্রশান্তি, বন্ধুতা-ভালবাসা ও দয়া-সহানুভূতির ভাবধারার স্থিতিলাভই হয় তার কাম্য। বংশের ধারা অব্যাহত রেখে মানবতার অগ্রগতিকে স্থায়িত্ব দান তার চরম লক্ষ্য। কুরআন মজীদে আল্লাহ্ তা’আলা বলেছেনঃ (আরবী****************)
আল্লাহ্ তা’আলা তোমাদের নিজেদের মধ্য থেকেই তোমাদের জন্যে জুড়ি বানিয়ে দিয়েছেন এবং তোমাদের এ জুড়ি থেকেই সন্তান-সন্ততি ও নাতিপুতি বানানর ব্যবস্থা করেছেন।
এ কারণে বিয়ে সব সময়ই স্থায়ী ভিত্তিতে হওয়া উচিত। কিন্তু সাময়িক বা অস্থায়ী বিয়ে সে রকম হয় না। তা হয় একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ পারিশ্রমিকের বিনিময়ে একটা নির্দিষ্ট সময়কালের জন্যে। ফলে বিয়ের যে তাৎপর্য কুরআনের আলোকে উপরে বলা হলো, তা এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। রাসূলে করীম (সা) শরীয়তের বিধান পূর্ণত্ব ও স্থিতি লাভের পূর্বে এরূপ বিয়ের অনুমতি দিয়েছিলেন। এ অনুমতির ক্ষেত্রেও সময় ছিল দীর্ঘদিনের সফর ও যুদ্ধযাত্রা, কিন্তু পরে তিনি নিজেই তা চিরদিনের তরে হারাম করে দিয়েছেন।
শুরুতে এরূপ বিয়ের অনুমতি দেয়ার কারণ ছিল। তখন মানুষ জাহিলিয়াত ত্যাগ করে ইসলামের দিকে যাওয়ার একটা ক্রান্তিলগ্ন বা সন্ধিক্ষণের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছিল। জাহিলিয়াতের যুগে জ্বেনা ব্যভিচার ছিল সহজ, অবাধ, সর্বপ্রকার বাধামুক্ত।
ইসলাম আগমনের পর এ লোকদেরই যখন জিহাদের জন্যে দূরদেশে দীর্ঘ দিনের জন্যে যাত্রা করতে হয়, তখন তাদের স্ত্রীদের থেকে এতদিন বিচ্ছিন্ন ও নিঃসম্পর্ক থাকা খুব কষ্টকর হয়ে দাড়াল। এদিকে নও-মুসলিমদের মধ্যে যেমন খুব শক্ত ঈমানদার লোক ছিলেন, তেমনি ছিলেন দুর্বল ঈমানদারও। বিশেষ করে দুর্বল ঈমানদার লোকদের ব্যাপারে তাদের জ্বেনায় লিপ্ত হয়ে পড়ার আশংকা তীব্র হয়ে দেখা দিল অথচ তা সর্বাধিক নির্লজ্জতার পাপ ও বীভৎস কাজ।
অপরদিকে শক্ত ঈমানদার লোকেরা নিজেদের ‘খাসি’ বানিয়ে যৌন শক্তিকে দমন করে রাখার সংকল্প গ্রহণ করলেন! এ পর্যায়ে হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বলেছেনঃ (আরবী****************)
আমরা রাসূলে করীম (সা)-এর সঙ্গে যুদ্ধযাত্রা করতাম। এ সময় আমাদের স্ত্রীরা আমাদের সঙ্গে থাকত না। তখন আমরা বললাম, আমরা কি ‘খাসি’ হয়ে যাব? কিন্তু নবী করীম (সা) আমাদের সে কাজ করতে নিষেধ করলেন এবং কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে কাপড় ইত্যাদির বিনিময়ে বিয়েক করার অনুমতি দিলেন।
এভাবে এ সাময়িক বিয়ের অনুমতি হয়, (আরবী) ভাষায় একেই বলা হয় ‘মুতয়া’ বিয়ে। আর তা হয় দুর্বল ও শক্তিশালী ঈমানদার উভয় শ্রেণীর মুসলমানের সাময়িক কষ্ট ও সমস্যা দূর করার উদ্দেশ্যে। ইসলাম মুসলমানদের বিবাহিত ও দাম্পত্য জীবনের জন্যে শরীয়তের যে বিধান চালু করতে চেয়েছিল, এটা ছিল সেই দিকেরই একটি পদক্ষেপ। ইসলামের লক্ষ্য ছিল এমন এক বৈবাহিকও দাম্পত্য জীবন-বিধান উপস্থাপন, যা বিয়ের সকল উদ্দেশ্যকেই বাস্তবায়িত করবে। আর তা হচ্ছে চরিত্রের পবিত্রতা, সতীত্ব রক্ষা, বিবাহিত জীবনের স্থায়ীত্ব বিধান, বংশ ধারা অব্যাহত রাখা, প্রেম-প্রীতি-ভালবাসা ও পারিবারিক জীবনের পরিধি বৈবাহিক সম্পর্কের সূত্রে প্রশস্ততর করা।
কুরআন যেমন করে মদ্যপান ও সুদ হারাম করায় ক্রমিক পদ্ধতি অবলম্বন করেছে-জাহিলিয়াতের যুগে এ দুটো সর্বত্র ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে ছিল-জ্বেনা হারাম করা ও লজ্জাস্থানের মর্যাদা রক্ষার ক্ষেত্রেও অনুরূপভাবে ক্রমিক নিয়ম অবলম্বন করেছে। তাই প্রথম দিকে প্রয়োজনের দৃষ্টিতে ‘মুতয়া’ বিয়ের অনুমতি দিয়েছেন। পরে এ ধরনের বিয়েকে নবী করীম (সা) সম্পূর্ণ হারাম ঘোষণা করেছেন। হযরত আলী ও বহু সাহাবীর সূত্রে এ পর্যায়ে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। হযরত মাবুরাতা আল-জুহানী থেকে বর্ণিত হয়েছেঃ (আরবী****************)
তিনি নবী করীম (সা)-এর সঙ্গে মক্কা বিজয় অভিযানে গমন করেছিলেন। এ সময় তিনি তাদের অনুমতি দিয়েছিলেন মুতয়া পন্থায় স্ত্রী গ্রহণের। তিনি আরও বলেনঃ কিন্তু নবী করীম (সা) মক্কা থেকে বের হয়ে আসার পূর্বেই তা হারাম করে দেন।
তাঁরই বর্ণিত অপর একটি হাদীসের ভাষা হচ্ছেঃ (আরবী****************)
আর আল্লাহ্ তা’আলা এ বিয়েকে কিয়ামত পর্যন্ত সময়ের জন্যে হারাম করে দিয়েছেন।
এক্ষণে প্রশ্ন উঠেছে, এই হারাম ঘোষণা কি একনও কার্যকর, এখনও তা অব্যাহত হয়ে আছে, যেমন মা, কন্যা বিয়ে করা চিরকালের তরে হারাম কিংবা এই হারাম করণটা কি মৃত জীব, রক্ত ও শূকর গোশত হারাম হওয়ার মতো?...... তাহলে প্রয়োজন দেখা দিলেও জ্বেনার মধ্যে পড়ার আশংকা তীব্র হলে তখন এরূপ বিয়ে মুবাহ হয়ে যাবে?
সাধারণভাবে সমস্ত সাহাবী সমাজ এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ এক মত যে, ‘মুতয়া’ বিয়ে চিরতরে ও চূড়ান্তভাবে হারাম, পূর্বের সেই হারাম ঘোষণা এখনও পূর্ণ মাত্রায় কার্যকর ও অব্যাহত ও অপরিবর্তিত হয়ে আছে। শরীয়ত চূড়ান্ত রূপ লাভ করেছে বলে এক্ষণে তাতে এ ধরনের বিয়ের কোন অবকাশ থাকতে পারে না।
অবশ্য হযরত ইবনে আব্বাব (রা) ভিন্নমত প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন, উত্তরকালেও প্রয়োজনের কারণে তা জায়েয ও মুবাহ। একজন লোক তাঁর কাছে ‘মুতয়া’ নিয়মে স্ত্রী গ্রহণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি তাকে অনুমতি দিয়েছিলেন। তাঁর গোলাম তাঁকে জিজ্ঞেস করলঃ খুব শক্ত ও কঠিন ঠেকার সময়ই কি তা জায়েয? ইবনে আব্বাস (রা) বললেনঃ হ্যা।
পরবর্তীকালে তিনি নিজেই যখন জানতে পারলেন যে, লোকেরা এক্ষেত্রে বেশ বাড়াবাড়ি শুরু করেছে এবং প্রয়োজন ছাড়াও এই পন্থা অবলম্বন করছে, তখন তিনি তাঁর এই মত প্রত্যাহার করেন এবং এর সমর্থনে ফতওয়া দেয়াও বন্ধ করে দেন। (আরবী****************)
একসঙ্গে একাধিক স্ত্রী গ্রহণ
ইসলাম প্রকৃতির সাথে পুরামাত্রায় সামঞ্জস্যশীল দ্বীন। বাস্তবতার সাথে মুকাবিলা করার যোগ্যতাসম্পন্ন এক পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। তা যেমন অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি থেকে মানুষকে বিরত রাখে, তেমনি প্রয়োজনের তুলনায় কোন অসম্পূর্ণতা অক্ষমতাই তাতে নেই। একসঙ্গে একাধিক স্ত্রী রাখার অনুমতি তাতে রয়েছে দেখে আমরা একথার বাস্তব প্রমাণ পাই। কেননা তা বহু মানবিক, ব্যক্তিগত ও সামাজিক গুরুতর প্রয়োজনে একসঙ্গে একাধিক স্ত্রী রাখার অনুমতি দিয়েছে মুসলমানকে।
ইসলামের পূর্বে বিভিন্ন জাতি ও ধর্মানুসারী জনগোষ্ঠির মধ্যে বহু সংখ্যক মেয়েলোককে এক-এক ব্যক্তির স্ত্রীত্বে গ্রহণ করার ব্যাপক প্রচলন ছিল। কোন কোন সময় তাদের সংখ্যা দশজনকেও ছাড়িয়ে যেত, একশ দুশ তিনশ পর্যন্তও পৌছে যেত এবং তাতে কোনরীপ শর্ত আরোপ করা হতো না, থাকত না কোনরূপ বাধা-বন্ধন। কিন্তু দ্বীন-ইসলাম এসে এই একাধিক স্ত্রী গ্রহণের ক্ষেত্রে বিশেষ নিয়ম, শর্ত ও নিয়ন্ত্রণ কার্যকর করেছে।
প্রথম নিয়ন্ত্রণ হচ্ছে, ইসলাম একসঙ্গে ও এক সময়ে চারজন স্ত্রী গ্রহণের শেষ সীমা নির্ধারিত করেছে। গাইলান আস মাকাফী নামক এক ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে। তখন তার স্ত্রীত্বে দশজন মেয়েলোক ছিল। নবী করীম (সা) তাকে বললেনঃ (আরবী****************)
তুমি এদের মধ্যে থেকে চারজন গ্রহণ কর। আর অবশিষ্টদের বিচ্ছিন্ন করে দাও।
অনুরূপভাবে ইসলাম গ্রহণকালে যার আটজন বা পাঁচজন স্ত্রী থাকত তাকেও রাসূলে করীম (সা) চারজনের অধিক রাখতে নিষেধ করে দিলেন।
তবে নবী করীম (সা)-এর নিজের এক সঙ্গে নয়জন স্ত্রী রাখার ব্যাপারটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরনের। আল্লাহ্ তা’আলা তাঁকে দাওয়াতী কাজের প্রয়োজন এবং তাঁর অন্তর্ধানের পর মুসলিম উম্মতের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে এরূপ করার বিশেষ অনুমতি দিয়েছিলেন।
একসঙ্গে একাধিক স্ত্রী গ্রহণের শর্ত- সুবিচার
একসঙ্গে একাধিক স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি ইসলাম দিয়েছে এ শর্তে যে, ব্যক্তির নিজের দৃঢ় প্রত্যয় থাকতে হবে যে, সে তাঁর স্ত্রীদের মধ্যে পূর্ণ সুবিচার রক্ষা করতে পারবে। খাওয়া-পরা-রাত যাপন করা ও ব্যয়ভার বহনের দিক দিয়ে।
যে লোক পূর্ণ সুবিচার ভারসাম্য ও সমতার মাঝে এ সব অধিকার যথাযথভাবে আদায় করতে পারবে বলে নিজের সম্পর্কে দৃঢ় প্রত্যয়ের অধিকারী নয়, তার পক্ষে একাধিক স্ত্রী গ্রহণ সম্পূর্ণ হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা’আলার বাণীঃ (আরবী****************)
যদি তোমরা সেই সুবিচার করতে পারবে না বলে ভয় পাও তাহলে মাত্র একজন স্ত্রী গ্রহণ করবে।
আর নবী করীম (সা) বলেছেনঃ (আরবী****************)
যে লোকের দুজন স্ত্রী এবং সে তাদের মধ্যে একজনকে অপরজনের ওপর অগ্রাধিকার দেয়, সে কিয়ামতের দিন তার পড়ে যাওয়া বা ঝুঁকে পড়া এক পার্শ্ব টানতে টানতে উপস্থিত হবে।
এ হাদীসে দুজনের একজনের প্রতি ঝুঁকে পড়া সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। এই ঝুঁকে পড়ার অর্থ অপরজনের ন্যায্য অধিকার হরণ করা, তার প্রতি অবিচার করা। নিছক মনের ঝোঁকে কোন গুনাহ্ নয়। কেননা মনের টান বা ঝোঁক এমন একটা ব্যাপার, যার ওপর কারো ইচ্ছামূলক কোন ক্ষমতা নেই। আর সেজন্যে আল্লাহ্ তা’আলা এ ব্যাপারে কাউকে পাকড়াও করেন না এবং এই ত্রুটি ধর্তব্যের মধ্যে গণ্য হবে না। আল্লাহ্ নিজেই বলেছেনঃ (আরবী****************)
তোমরা শত চাইলেও তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে (আদর্শ স্থানীয় এ পূর্ণ মাত্রায়) সুবিচার ও ভারসাম্য রক্ষা করতে সক্ষম হবে না। কাজেই কোন একজনের প্রতি পূর্ণ মাত্রায় ঝুঁকে পড়া পরিহার করে চল।
এ কারণেই নবী করীম (সা) সব বন্টন করতেন ও তাতে সুবিচার করতেন তাঁর বেগমদের মধ্যে এবং সেই সঙ্গে বলতেনঃ (আরবী****************)
হে আল্লাহ্ আমি আমার সাধ্যমত সুবিচারপূর্ণ বন্টন করলাম। তাই আমার সাধ্যের অতীত ও তোমার ক্ষমতাভুক্ত যে ইনসাফ তা করতে না পারার দরুন আমাকে তুমি পাকড়াও করো না।
এই সাধ্যের অতীত বলে বুঝিয়েছেনঃ মনের ঝোঁক ও টান কেবলমাত্র বিশেষভাবে একজনের প্রতি মনের মাত্রাতিরিক্ত টান- প্রেম-ভালবাসা থাকা কিছুমাত্র অস্বাভাবিক নয়। এ ব্যাপারে মানুষ অনেক সময় অক্ষম হয়ে যায়, হয় একান্তই অসহায়।
নবী করীম (সা) যখন বিদেশ সফরে ইচ্ছা করতেন, তখন স্ত্রীদের মধ্যে যাঁর নাম কুরআনে’র মাধ্যমে জানা যেত, তকেই সঙ্গে নিয়ে রওয়ানা হতেন।
একাধিক স্ত্রী গ্রহণের অনুমতির যৌক্তিকতা
বস্তুত ইসলাম আল্লাহ্ তা’আলার সর্বশেষ দ্বীন, সর্বশেষ নবী ও রাসূলের মাধ্যমে অবতীর্ণ জীবন বিধান। তা এক চিরন্তন ও সর্বসাধারণ্যে প্রযোজ্য শরীয়ত উপস্থাপিত করেছে। মানব জীবনের সকল দিক ও বিভাগ সম্পর্কিত আইন-বিধান তাতে বিদ্যমান। সর্বকালে, সর্বযুগে ও সর্বদেশে তা প্রয়োগযোগ্য ও নিশ্চিত কার্যকর। প্রতিটি মানুষই তার জীবন-সমস্যার সমাধান তা ফেকে লাভ করতে পারে। তাতে নগরবাসীর জন্যে বিধান রয়েছে, গ্রাম বা প্রান্তরবাসীর জন্যে নয় কিংবা শীতপ্রধান দেশের লোকদের জন্যে বিধান কয়েছে, গ্রীষ্মপ্রধান দেশের লোকদের প্রয়োজনাবলীর প্রতি ভ্রূক্ষেপ করা হয়নি- এ শরীয়ত তেমন নয়। অথবা এরূপও নয় যে, তাতে এককালের এক বংশের লোকদের প্রয়োজন পূরণ করা হয়েছে, অপর কোন কালের বা বংশের লোকেরা তা থেকে বিধান লাভ করতে পারে না।
বস্তুত তা যেমন ব্যক্তিদের প্রয়োজন পূরণ করে, তেমনি করে সমাজ ও সমষ্টিরও। নির্বিশেষে সমগ্র মানুষের কল্যাণের সুষ্ঠু ব্যবস্থা তাতে রয়েছে।
লোকদের বিচিত্র অবস্থা লক্ষণীয়। কেউ তার বংশের ধারা অব্যাহত রাখতে ইচ্ছুক; কিন্তু তার স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও তার একটিও সন্তান নেই। তার কারণ বন্ধ্যাত্ব রোগ কিংবা অন্য যা-ই হোক না কেন। এরূপ অবস্থায় সে স্ত্রীর জন্যে কি সম্মানজনক এবং সে ব্যক্তির জন্যে উত্তম পন্থা এ নয় যে, সে লোকটি তার প্রথম স্ত্রীকে নিজের সঙ্গে রেখে এবং তার প্রাপ্য যাবতীয় অধিকার যথাযথভাবে আদায় করতে থাকে আর একজন স্ত্রী গ্রহণ করবে, যেন তার সন্তান লাভের স্বাভাবিক কামনা-বাসনা পূর্ণ হতে পারে।
কোন কোন মানুষের যৌন শক্তি খুব প্রবল ও প্রচণ্ড হতে পারে। যৌন আবেগ ও উত্তেজনা তার জন্যে অদম্য হতে পারে। কিন্তু স্ত্রী সেদিক দিয়ে অনাসক্তা বা অনাগ্রহী অথবা অক্ষম কিংবা হতে পারে সে চিররুগ্না, স্বামীর দাবি পূরণে অসমর্থ। স্ত্রীর ঋতুকাল দীর্ঘতার হতে পারে, আর তার স্বামী সেজন্য দীর্ঘদিন ধৈর্য ধারণ করে থাকতে অক্ষম। এরূপ অবস্থায় কোন বালিকা বন্ধু (girl friend) গ্রহণ করার পরিবর্তে শরীয়তাসম্মতভাবে আর একটি বিয়ে করা কি তার জন্যে শোভন নয়?
অনেক সময় দেশে পুরুষদের তুলনায় মেয়েদের সংখ্যা অনেক বিশি হয়ে থাকে। বিশেষ করে জাতীয় যুদ্ধে যখন যুবকরা দলে দলে প্রাণ দান করে, তখন তো বহু মেয়েই স্বামীহারা হয়ে জীবন কাটাতে বাধ্য হয়। কেননা তাদের বিয়ে করার মতো পুরুষ খুঁজে পাওয়া যায় না। অনুরূপ অবস্থায় সমাজের সার্বিক কল্যাণ এবং বিশেষ করে নারী সমাজের কল্যাণ এতেই হতে পারে যে, তারা দাম্পত্য জীবন বঞ্চিত ও কুমারী বৃদ্ধা হয়ে থাকার পরিবর্তে ‘সতীন’ হয়ে থাকাকে অগ্রাধিকার দেবে। তার ফলে তারা স্ত্রীত্বের মর্যাদা ও স্বামীর প্রেম-ভালবাসা, মানসিক প্রশান্তি ও নৈতিক পবিত্রতা সহকারে জীবন অতিবাহিত করার সুযোগ লাভ করতে পারবে। হতে পারবে সন্তানের মা। এরূপ জীবনধারাই তো প্রকৃতপক্ষে তাদের প্রকৃতির প্রতিধ্বনী।
পুরুষ সংখ্যার তুলনায় অধিক সংখ্যক বিবাহক্ষম নারীদের নিম্নোক্ত তিনটি অবস্থার মধ্যে যে কোন একটি দেখা দেয়া অনিবার্যঃ
-হয় তারা জীবনভর বঞ্চনার তিক্ত বিষ পান করতে থাকবে ও এভাবেই গোটা জীবন অতিবাহিত করবে;
-অথবা তারা মুক্ত-স্বাধীন স্বেচ্ছাচারী হয়ে পুরুষদের খেলার পুতুল ও লালসার ইন্ধন হয়ে জীবন নিঃশেষ করবে;
-কিংবা ব্যয়ভার বহনে সক্ষম ও শুভ আচরণ গ্রহণে আগ্রহী বিবাহিত পুরুষদের সাথে তাদের বিয়ে হওয়াকে বৈধ মনে করা হবে।
অনাসক্ত ও সুবিবেচকদের দৃষ্টিতে বিচার করলে নিঃসন্দেহে বোঝা যাবে যে, এ শেষোক্ত অবস্থাই সুবিচার ও ভারসাম্যপূর্ণ সমাধান। সামাজিক শৃঙ্খলা ও নৈতিক স্বাস্থ্যের দৃষ্টিতেও এ ব্যবস্থাই উত্তম। আর ইসলাম এ সমাধানই পেশ করেছে মানবীয় এ জটিল সমস্যাটির। আল্লাহ্ সত্যই বলেছেনঃ (আরবী****************)
আল্লাহর প্রতি দৃঢ় প্রত্যয়শীল লোকদের জন্যে আল্লাহর দেয়া বিধানের তুলনায় উত্তম বিধান আর কে দিতে পারে? (সূরা মায়িদাঃ ৫০)
ইসলামে একসঙ্গে একাধিক স্ত্রী গ্রহণের অনুমতির মৌল তত্ত্ব ও প্রসঙ্গ কথা এ-ই। অথচ পাশ্চাত্য খ্রিস্টান পাদ্রীরা এটা নিয়েই মুসরমানদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটিয়ে পৃথিবীব্যাপী ঝড় তুলেছে। কিন্তু তাদের নিজেদের অবস্থা হচ্ছে এই যে, তারা পুরুষদের জন্যে অসংখ্য প্রেমিক-বান্ধবী-রক্ষিতা রাখার অবাধ সুযোগ ও অনুমতি দিয়েছে এবং তাতে কোনরূপ আইন বা নৈতিকতার নিয়ন্ত্রণ কার্যকর করেনি। এহেন নৈতিকতা ও ধর্মবিবর্জিত কার্যক্রমের ফল তারা লাভ করছে অসংখ্য অবৈধ অনাথ সন্তান রূপে। এর দরূন যে সামাজিক কলুষতার সৃষ্টি হয়েছে, তা অকথ্য ও দুরপনেয়। এ মহাসত্যের আলোকে কোন্ বিধানটি অধিকতর মানবিক ও কল্যাণকর পাশ্চাত্য না ইসলামের, তা অবশ্য গুরুত্ব সহকারে বিবেচ্য।
স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্ক
কুরআন মজীদ বিয়ের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে ও প্রাঞ্জলভাবে বর্ণনা করেছে। এ ভিত্তির ওপরই দাম্পত্য জীবনের প্রাসাদ রচিত হয়। যৌন উচ্ছৃঙ্খলতার পরিবর্তে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রেম-ভালবাসা, মানসিক শান্তি ও স্বস্তি, তৃপ্তি, স্বামী স্ত্রীর-উভয়ের আত্মীয়-স্বজন ও বংশ পরিবারের মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসার ও সম্প্রীতির গভীর সম্পর্ক, মানবীয় সহানুভূতি, সহৃদয়তা আবেগপূর্ণ সংবেদনশীলতার পূর্ণাঙ্গ প্রকাশ এবং পিতা-মাতা হিসেবে সন্তানদের সাথে আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে উঠা প্রভৃতিই হচ্ছে বৈবাহিক বন্ধনের আসল লক্ষ্য। সূরা আর-রুম-এর আয়াতে এ দিকেই ইশারা করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছেঃ (আরবী****************)
এবং তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে এও একটি যে, তিনি তোমাদের জন্যে তোমাদের মধ্য থেকেই জুড়ি সৃষ্টি করেছেন, যেন তোমরা তাদের কাছে পরম শান্তি স্বস্তি লাভ করতে পার এবং তোমাদের পরস্পরের মধ্যে বন্ধুত্ব ও সহৃদয়তার সৃষ্টি করেছেন। চিন্তাশীল ব্যক্তিদের জন্যে এতে বহু চিন্তা-বিবেচনার তত্ত্ব ও বিষেয়াদি রয়েছে।
স্বামী-স্ত্রীর সংবেদনশীল সম্পর্ক
এসব লক্ষ্য এ উদ্দেশ্য ছাড়াও স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সংবেদনশীল ও দৈহিক বা যৌন সম্পর্কের দিকে কুরআন মজীদে আলোকপাত করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রেও কুরআন মানুষকে সহজ সরল ঋজু পথ প্রদর্শন করেছে। তা অনুসরণ করে মানুষ পংকিল ও জঘন্য ভ্রান্ত পথ পরিহার করে স্বীয় স্বাভাবিক কামনা-বাসনা পূরণ করতে পারে।
হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, ইয়াহূদী ও অগ্নিপূজকরা স্ত্রীর হায়েয হলে তার থেকে অনেক দূরে চলে যেত এবং এ ব্যাপারে খুবই বাড়াবাড়ি করত। আর খ্রিস্টনরা এ অবস্থায়ও স্ত্রী সঙ্গম করত। হায়েযকে তারা কিছুমাত্র পরোয়া বা ঘৃণা করত না। আর জাহিলিয়াতের লোকেরা স্ত্রীর হায়েয হলে একঙ্গে পানাহার বা উঠা-বসা ও একই শয্যায় শয়ন- এমনকি একই ঘরে বসবাস পর্যন্ত পরিহার করত। ঠিক ইয়াহূদী ও অগ্নিপূজকদের মতো।
এসব দেখে কোন মুসলিমের মনে প্রশ্ন দেখা দেয়। এরূপ অবস্থায় স্ত্রীদের সাথে সংমিশ্রণের ক্ষেত্রে কি হালাল আর কি হারাম, তা তাঁরা রাসূলে করীম (সা)-এর কাছে জানতে চান। তখন নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয়ঃ (আরবী****************)
লোকেরা তোমার কাছে ‘হায়েয’ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। তুমি বল- তা খবেই কদর্য-পংকিল। এ অবস্থায় স্ত্রীদের থেকে বিচ্ছিন্ন থাক। তাদের সাথে দৈহিক নৈকট্য করো না, যতক্ষণ না তারা পবিত্র হচ্ছে। পরে যখন তারা পবিত্র হবে, তখন তোমরা তাদের কাছে যাও যেভাবে আল্লাহ্ তোমাদের জন্যে নিয়ম করে দিয়েছেন। আল্লাহ্ তওবাকারী ও পবিত্রতাবলম্বনকারীদের পছন্দ করেন।
এ আয়াতে স্ত্রীদের থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার আদেশ থেকে আরবের লোকেরা মনে করে নিয়েছিল যে, ওদের সাথে বসবাসও করা যাবে না। তখন নবী করীম (সা) আয়াতের সঠিক ব্যাখ্যা প্রদান করতে গিয়ে বললেনঃ (আরবী****************)
আমি তো তোমাদের আদেশ করেছি হায়েয অবস্থায় স্ত্রীদের সাথে সঙ্গম পরিহার করতে। অনারবদের ন্যায় তাদের ঘর থেকে বহিষ্কৃত করার আদেশ তো আমি দিইনি।
ইয়াহুদীরা যখন একথা জানতে পারল, তখন বললঃ এ লোকটি সব ব্যাপারে আমাদের বিরোধিতা করার সংকল্প নিয়েছে।
অতএব স্ত্রীর হায়েয অবস্থায় তার সাথে সঙ্গম করা ছাড়া- ময়লার স্থান পরিহার করে- অন্যান্যা সব ব্যাপারে তার থেকে সুখ লাভ করায় মুসলমানের পক্ষে কোন দোষ নেই। এ থেকে দেখা গেল একদিকে হায়েয অবস্থায় স্ত্রীদের ঘর থেকে বহিষ্কৃত করা এবং অপরদিকে তাদের সাথে যৌন মিলন পর্যন্ত মেলামেশা করা, এ দুই প্রান্তিক নীতির মধ্যবর্তী ভারসাম্যপূর্ণ ও সামঞ্জস্যসম্পন্ন নীতির প্রবর্তন করেছে।
আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান উদঘাটন করেছে, হায়েয নিষ্ক্রান্ত রক্তে এক ধরনের বিষাক্ত বস্তু থাকে, যা দেহের মধ্যে থেকে গেলে তা খুব ক্ষতিকর হয়ে দেখা দেয়। ‘হায়েয’ অবস্থায় যৌন সঙ্গম পরিহার করার তত্ত্বত উদঘাটিত হয়েছে। জানা গেছে, হায়েয অবস্থায় রক্ত জমা হওয়ার কারণে স্ত্রীলিঙ্গ সংকুচিত হয়ে থাকে। আভ্যন্তরীণ শীরা-উপশিরাসমূহ বহমান হওয়ার কারণে স্নায়ু নিচয় খুবই অস্থির ও অস্বাভাবিক অবস্থায় থাকে। কাজেই এরূপ অবস্থায় যৌন সঙ্গম হলে তার জন্যে ক্ষতিকর হয়ে দেখা দেয়। অনেক সময় হায়েয বন্ধ হয়ে যেতে পারে। আর তাতে স্নায়ুবিক রোগের সৃষ্টি হয়। অনেক সময় যৌন অঙ্গে জ্বালানিরও উদ্ভব হয়। (ডাঃ আবদুল আযীয ইসমঈল কৃতঃ (আরবী****************) দ্রষ্টব্য)
গুহ্যদ্বার পরিহার
স্ত্রীদের সাথে দৈহিক সম্পর্ক পর্যায়ে সূরা আল-বাকারার এ আয়াতটি নাযিল হয়ঃ (আরবী****************)
স্ত্রীরা তোমাদের ক্ষেত। তাই তোমরা ক্ষেতে গমনাগমন কর যেমন তোমরা চাও। আর নিজেদের ভবিষ্যতের সামগ্রী বানাও। আল্লাহকে ভয় কর। জেনে রাখ, তোমাদের তাঁর সাথে অবশ্যই সাক্ষাৎ হতে হবে। আর ঈমানদার লোকদের সুসংবাদ শোনাও।
এ আয়াতটি নাযিল হওয়ার বিশেষ কারণ ও যৌক্তিকতা হয়েছে। শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ দিহলভী তার উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেনঃ
ইয়াহূদীরা স্ত্রী সঙ্গম পর্যায়ে কোনরূপ আল্লাহ্ প্রদত্ত নির্দেশ ছাড়াই শুধুই সংকীর্ণতার সৃষ্টি করেছিল। আর তাদের কাছাকাছি বসবাসকারী আনসার সমাজের লোকেরা তাদেরই পন্থা অনুসরণ করত। তারা বলতঃ স্ত্রীর পেছন থেকে সম্মুখে (স্ত্রীর অঙ্গে) সঙ্গম করা হলে সন্তান টেরা হয়। তখন কুরআনের এ আয়াত নাযিল হয়ঃ (আরবী****************)
তোমরা তোমাদের ক্ষেতে গমনাগমন কর যেভাবে তোমরা চাও।
অর্থাৎ সঙ্গম তো স্ত্রীর যৌন অঙ্গেই হবে- তা সম্মুখ দিক থেকে হোক কিংবা হোক বাইরের দিক অর্থাৎ পেছনের দিক থেকে। যৌন সঙ্গমের কোন বিশেষ পন্থা বা পদ্ধতির কোন সম্পর্ক নেই সামাজিক-তমদ্দুনিক বা জাতীয় ব্যাপারাদির সাথে। তার পরে ব্যক্তিগত সুবিধা-অসুবিধার ব্যাপারে তো প্রত্যেক ব্যক্তি নিজেই জানে। এ ব্যাপারে ইয়াহূদীদের দৃষ্টি সংকীর্ণতা তাদের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মতার ফসল। এ কারণে তা প্রত্যাখ্যান করাই বাঞ্ছনীয়। (আরবী****************)
বস্তুত সঙ্গম কার্যের পদ্ধতি ও অবস্থার নির্ধারণ দ্বীন বা ধর্মের কর্ম নয়। মানুষ আল্লাহকে ভয় করবে আর আল্লাহর সাথে যে সাক্ষাৎ হবেই, একথা সে ভাল করে জেনে নেবে। এজন্যে সে গুহ্যদ্বার পরিহার করে চলবে। কেননা তা পায়খানার রাস্তা। এ কাজ তো পংকিল লেওয়াতাতের শামিল। শরীয়ত এ কারণেই তা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা জরুরী মনে করেছে। নবী করীম (সা) বলেছেনঃ (আরবী****************)
তোমরা স্ত্রীদের গুহ্যদ্বারে সঙ্গম করো না।
যে লোক তার স্ত্রীর গুহ্যদ্বারে সঙ্গম করে, রাসূলে করীম (সা) তাকে বলেছেঃ (আরবী****************)
ছোট লেওয়াতাতকারী।
আনসার বংশের একজন মহিলা পিছনের দিক দিয়ে স্ত্রী অঙ্গে সঙ্গম করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে নবী করীম (সা) তাকে এ আয়াতটি পাঠ করে শোনালেনঃ (আরবী****************)
তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের ক্ষেত। অতএব তোমরা তোমাদের ক্ষেতে আস যেভাবেই ও যে দিক দিয়েই তোমরা চাও।
হযরত উমর (রা) জিজ্ঞেস করলেনঃ (আরবী****************)
হে রাসূল! আমি তো ধ্বংস হয়ে গেছি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কোন জিনিস তোমাকে ধ্বংস করল? বললেনঃ গতরাতে আমার সওয়ারীর দিক বদল হয়ে গিয়েছিল। (অর্থাৎ পিছন থেকে স্ত্রী অঙ্গে করেছি।)
একথা শুনে নবী করীম (সা) কোন জবাব দিলেন না। পরে উপরিউক্ত আয়াতটি নাযিল হয়। তার পরে নবী করীম (সা) বললেনঃ (আরবী****************)
সম্মুখ দিয়ে কর, পিছন দিয়েও করতে পার। তবে হায়েয অবস্থা ও গুহ্যদ্বার পরিহার করে চল। (আহমদ, তিরমিযী)
স্বামী-স্ত্রীর গোপন তত্ত্ব সংরক্ষণ
কুরআন মাজীদে নেককার ও পরহেযগার স্ত্রীলোকদের গুণপনা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছেঃ (আরবী****************)
বিনয়ী আল্লাহ্ অপ্রকাশিত বিষয়ের সংরক্ষণকারী আল্লাহর সংরক্ষণের অধীন ও আনুকূল্যে। (সূরা নিসাঃ ৩৪)
এ আয়াতে যেসব অদৃশ্য-গোপন বিষয়াদির সংরক্ষণের কথা বলা হয়েছে, স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক বিশেষ সম্পর্ক পর্যায়ের বিষয়-ব্যাপারাদিও তার মধ্যে রয়েছে। এসব গোপন তত্ত্বের উল্লেখ বন্ধ-বান্ধবীদের মজলিসে বৈঠকে-সভায় প্রকাশ করা নিষিদ্ধ।
হাদীসে বলা হয়েছেঃ (আরবী****************)
কিয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে অতীব নিকৃষ্টতম মর্যাদার হবে সে ব্যক্তি, যে স্ত্রীর কাছ থেকে স্বীয় প্রয়োজন পূর্ণ করে এবং পরে সে গোপন কথা প্রচার করে দেয়।
হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) আমাদের নামায পড়ালেন, সালাম ফিরিয়ে আমাদের দিকে মুখ করে বললেনঃ বসে থাক সকলে এবং শোন। তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে কে, যে নিজের স্ত্রীর কাছে গিয়ে ঘরের দুয়ার বন্ধ করে দেয় ও পর্দা ফেলে দেয়? পরে যখন বাইরে বের হয়ে আসে তখন লোকদের বলতে থাকে, আমি আমার স্ত্রীর সাথে এই এই করেছি?
রাসূলে করীম (সা)-এর এ প্রশ্নের কেউ কোন জবাব দিল না। পরে তিনি মহিলা নামাযীদের লক্ষ্য করে বললেনঃ তোমাদের মধ্যেও কি এমন কেউ আছে যে এ ধরনের কথাবার্তা বলে? একটি যুবতী নারী নিজ হাটুর ওপর ভর করে নবী করীম (সা)-কে দেখতে ও তাঁর কথা শুনতে চেষ্টা করছিল, সে বললঃ আল্লাহর কসম, পুরুষরাও এ রকম কথাবার্তা বলে। এ কথা শুনে নবী করীম (সা) বললেনঃ (আরবী****************)
যে লোক এরূপ করে তার দৃষ্টান্ত কি তা কি তোমরা জান? তার দৃষ্টান্ত শয়তান পুরুষ শয়তান নারীর মতো, যে নিজে স্ত্রীর সাথে রাজেপথে মিলিত হয় এবং স্বীয় প্রয়োজন পূরণ করে, আর সমস্ত মানুষ চোখ খুলে এ নির্লজ্জ দৃশ্য অবলোকন করে।
এ ধনের নির্বুদ্ধিতাজনক কাজের প্রতি চরম ঘৃণা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে একজন মুসলমানের জন্যে উপস্থাপিত দৃষ্টান্তই যথেষ্ট। কেননা এ অত্যন্ত জঘন্য কাজ। কোন মুসলমানই শয়তান-পুরুষ শয়তান-নারী হওয়া পছন্দ করতে পারে না।
পরিবার পরিকল্পনা
মানব জাতি ও মানব বংশের স্থিতিই বিয়ে ও বিবাহিত জীবনের চরম লক্ষ্য। আর এ স্থিতিই নির্ভরশীল হচ্ছে বংশধারা প্রবাহ অব্যাহতভাবে জারী থাকার ওপর। এ কারণে ইসলাম বংশবৃদ্ধির ওপর খুব বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছে এবং খুব বেশি পছন্দনীয় বলে ঘোষণা করেছে। ইসলামের দৃষ্টিতে সন্তান- ছেলেই হোক কি মেয়েই হোক- অতীব কল্যাণ ও সমৃদ্ধির উপকরণ। কিন্তু সেই সঙ্গে ইসলাম যুক্তি সঙ্গত কারণ ও গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনের দরুন পরিবার পরিকল্পন পদ্ধতি অবলম্বন করা যেতে পারে বলে মত প্রকাশ করেছে। রাসূলে করীম (সা)-এর যুগে জন্মহার প্রতিরুদ্ধ বা হ্রাস করার উদ্দেশ্যে আযল- শুক্র নিষ্ক্রমণকালে তা স্ত্রী-অঙ্গের বাইরে নিক্ষেপ- করার প্রচলন ছিল। রিসালত যুগে সাহাবিগণ এ পন্থা গ্রহণ করতেন। হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছেঃ (আরবী****************)
আমরা রাসূলে করীম (সা)-এর জীবদ্দশায় ‘আযল’ করতাম, অথচ তখন কুরআন নাযিল হচ্ছিল। অপর হাদীসের ভাষা হচ্ছেঃ (আরবী****************)
আমরা রাসূলে করীম (সা)-এর জীবদ্দশায় ‘আযল’ করতাম। এ সংবাদ তাঁর কাছে পৌছলে তিনি আমাদের এ কাজ থেকে নিষেধ করেন নি।
আর একটি হাদীসে বলা হয়েছেঃ (আরবী****************)
এক ব্যক্তি নবী করীম (সা)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে বললঃ হে রাসূল! আমর একশটি দাসী আছে, আমি তার সাথে ‘আযল’ করি এবং সে গর্ভবতী হোক- তা আমি পছন্দ করি না। আর পুরুষরা যা সাধারণত চায়, আমিও তাই চাই। ওদিকে ইয়াহূদীরা বলে বেড়াচ্ছে যে, ‘আযল’ হচ্ছে ছোটখাটো গোপন হত্যা। তখন নবী করীম (সা) বললেন, ইয়াহূদীরা মিথ্যা বলছে। আল্লাহ্ বাচ্চা জন্মাতে চাইলে তুমি তা রুখতে পার না।
রাসূলে করীম (সা)-এর এ কথাটির তাৎপর্য হচ্ছে, ‘আযল’ করা সত্ত্বেও শুক্রকীট গর্ভধারে পৌঁছে যেতে পারে এবং অজ্ঞাতসারেই গর্ভের সঞ্চার হওয়া সম্ভব।
হযরত উমর ফারূক (রা)-এর মজলিসে ‘আযল’ সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছিল। একজন বললেন, লোকেরা তো তাকে ‘ছোট গোপন হত্যা’ মনে করে। একথা শুনে হযরত আলী (রা) বললেনঃ ‘মওদাহ’ জীবন্ত প্রোথিত করা অর্থাৎ ‘সন্তান হত্যা’ বলা যেতে পারে তখন, যখন ভ্রূণ সাতটি পর্যায়ে অতিক্রম করে যায় অর্থাৎ মাটির নির্যাস শুক্রকীটে পরিণত হয়, পরে তা জমাটবাঁধা রক্ত রূপ লাভ করে, পরে তা হয় মাংসপিণ্ড, তার পরে অস্থিমজ্জা গড়ে উঠে, আর তার ওপর গোশত জমে। এসব পর্যায়ে অতিক্রম করেই মানবীয় আকার-আকৃতি লাভ করে। হযরত উমর (রা) বললেনঃ আপনি ঠিকই বলেছেন। আল্লাহ্ আপনাকে দীর্ঘায়ূ করুন।
কোন্ অবস্থায় পরিবার পরিবার পরিকল্পনা জায়েয
মাত্র কয়েকটি বিশেষ প্রয়োজনে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণ জায়েয হতে পারে। একটি প্রয়োজন হচ্ছে, মা’র জীবন বা স্বাস্থ্যের ওপর যদি রোগ বা প্রসবকালীন সংকটের দরুন হুমকি দেখা দেয়, তাহলে এ পদ্ধতি গ্রহণ করা যেতে পারে। এ সংকট বা হুমকির কথা অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে জানা যাবে, কিংবা কোন বিশ্বস্ত নির্ভরযোগ্য চিকিৎসাবিদ তা বলে দেবে। আল্লাহ্ নিজেই বলেছেনঃ (আরবী****************)
তোমরা নিজেদের হাতেই নিজেদের ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করো না।
বলেছেনঃ (আরবী****************)
তোমরা নিজেরাই নিজেদের হত্যা করো না। আল্লাহ্ নিশ্চয়ই তোমাদের প্রতি অতীব দয়াবান।
দ্বিতীয় ভিত্তি হচ্ছে, বৈষয়িক অসুবিধা, সমস্যা ও অনিশ্চয়তা-অসহায়ত্বের মধ্যে পড়ে যাওয়ার আশংকা, যার দরুন দ্বীনী সমস্যা দেখা দিতে পারে বলে মনে করা হবে। যার ফলে মানুষ সন্তানাদির কারণে হারাম জিনিস গ্রহণ ও অবৈধ কাজে লিপ্ত হওয়ার পরিণতি দেখা দেবে। আল্লাহ্ বলেছেনঃ (আরবী****************)
আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি সহজতার বিধান করতে চান, তোমাদের কোন অসুবিধায় ফেলতে চান না। (সূরা বাকারাঃ ১৮৫)
(আরবী****************)
আল্লাহ্ তোমাদের ওপর সংকীর্ণ বা অসুবিধা চাপিয়ে দিতে চান না।
তৃতীয় হচ্ছে, সন্তানদের স্বাস্থ্য নষ্ট হওয়ার কিংবা তাদের সঠিক লালন-প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে ব্যর্থ হওয়ার আশংকা। এ পর্যায়ে উল্লেখ্য হাদীসঃ (আরবী****************)
হযরত উসামা ইবনে যায়দ থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূলে করীমের কাছে উপস্থিত হয়ে বললঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ। আমি আমার স্ত্রীর সাথে আযল করে থাকি। তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ তুমি তা কেন কর? বললঃ আমি তার স্তনের ব্যাপারে আশংকা বোধ করি। তখন নবী করীম (সা) বললেনঃ ক্ষতি হওয়ার ভয় যদি যথার্থই হতো, তাহলে পারস্যবাসী ও রোমানবাসীদের ক্ষতি সাধিত হতো।
এ কথার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, নবী করীম (সা)-এর মতে ব্যক্তিদের ব্যাক্তিগত পর্যায়ে এ কাজ করা হলে সামষ্টিকভাবে গোটা উম্মতের জন্যে কোনরূপ ক্ষতিকর ছিল না। আর তা যে ক্ষতিকর নয়, তার বড় প্রমাণ এই যে, পারস্য ও রোমান জাতি এ সময় বড় শক্তিশালী সরকার ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার অধিকারী ছিল, তাদের তো এ কাজের দরুন কোন ক্ষতি হয়নি।
শরীয়তের দৃষ্টিতে আরও একটি প্রয়োজনের উল্লেখ করা যায়। তা হচ্ছে দুগ্ধপোষ্য শিশুর মা’র আবার গর্ভসঞ্চার হলে শিশুর পক্ষে ক্ষতিকর হতে পারে। কেননা তখন মা’র দুগ্ধ নষ্ট হয়ে যেতে পারে, যার ফলে শিশু দুর্বল হয়ে পড়তে পারে।
নাবী করীম (সা) উম্মতের জন্যে সামষ্টিকভাবে কল্যাণকর কার্যাদি করার হেদায়েত দিতেন। আর যে সব কাজের ফলে উম্মতের ক্ষতি সাধিত হওয়ার আশংকা, তা পরিহার করে চলতে বলতেন। নবী করীম (সা)-এর এ কথাটি সেই পর্যায়েরঃ (আরবী****************)
তোমরা তোমাদের সন্তানদের গোপন পন্থায় ধ্বংস করবে না। কেননা দুগ্ধপায়ী শিশুর বর্তমানে স্ত্রী সঙ্গম করলে শিশুর ক্ষতি হতে পারে।
কিন্তু নবী করীম (সা) এ কাজকে হারাম ধরে নিয়ে নিষেধ করেন নি। কেননা তাঁর সময়ে অন্যান্য জাতির লোকেরা এই পন্থা গ্রহণ করেছিল। কিন্তু তাতে তাদের কোন ক্ষতি হচ্ছিল না। শিশুকে দুধ খাওয়ানের কালে তদ্দরুন স্ত্রী সঙ্গম যদি চূড়ান্তভাবে নিষিদ্ধ করে দেয়া হতো তাহলে তাদের স্বামীদের তাতে কষ্ট হতো। দুগ্ধ সেবনের মেয়াদকাল দুই বছর পর্যন্ত চলতে থাকে। এ সব ব্যাপারের দিকে লক্ষ্য রেখে নবী করীম (সা) বলেছেনঃ (আরবী****************)
দুগ্ধপায়ী শিশুর মা’র সাথে সঙ্গম করতে আমি নিষেদ করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু পারস্য ও রোমকদের সম্পর্কে আমি জানতে পারলাম যে, তারা এ কাজ করে; কিন্তু তাতে তাদের সন্তানের কোন ক্ষতি হয় না।
আল্লামা ইবনুল কাইয়্যেম উপরিউদ্ধৃত হাদীসদ্বয়ের মাঝে সমন্বয় বিধানের জন্যে একটি বিশ্লেষণ দিয়েছেন। তিনি বলেছেনঃ
নবী করীম (সা)-এর সম্মুখে দুটি দিকই ছিল। একটি হচ্ছে দুগ্ধ পোষ্য শিশুর বর্তমানে তার মা’র মাথে সঙ্গম করলে শিশুর ক্ষতি হওয়ার আশংকা। যদিও সে ক্ষতিটা হত্যা বা ধ্বংস করার পর্যায়ের নয়, তা সত্ত্বেও ক্ষতির আশংকার দরুন তিনি তা নিষেধ করেছেন। কিন্তু তা হারাম ঘোষণা করা হয়নি, পরে তিনি ‘নিমিত্ত বন্ধকরণ’ হিসেবে তা থেকে বিরত রাখতে চেয়েছেন। কিন্তু তাঁর সম্মুখে অপর একটি দিকও উদঘাটিত হয়। তা হচ্ছে দুদ্ধ সেবনের মেয়েদের মধ্যে সঙ্গম নিষিদ্ধ হলে যে অসুবিধা ও বিপরীত হতে পারে, এই নিমেত্ত নিষিদ্ধকরণ দ্বারা তার প্রতিরোধ করা সম্ভবপর হবে না। বিশেষ করে নব্য যুবক ও যৌন উত্তেজনাসম্পন্ন ব্যক্তিদের চরম বিপর্যয়ে পড়ে যাওয়ার প্রবল আশংকা। এ কারণে তিনি মত গ্রহণ করলেন যে, এই কল্যাণ রোধ নিমিত্তরোধের বিপর্যয়ের তুলনয় অনেক প্রবল ও অগ্রাধিকার পাওয়ার দাবিদার। সেকালের দুটি বড় বড় প্রতিষ্ঠিত জাতির কর্ম পদ্ধতিও তার সম্মুখে প্রতিভাত ছিল। তারা এ কাজ পরিহার করেনি, এ সব কারণে তিনি এ কাজকে নিষিদ্ধ করেন নি।
আধুনিককালের গর্ভ বন্ধকরণের নব নব উপায় ও পন্থা উদ্ভাবিত হয়েছে। [ মনে রাখা আবশ্যক, গ্রন্থকার এখানে পরিবাব পরিকল্পনা পর্যায়ে কথা বলেছেন, জন্ম বন্ধ বা বন্ধ্যাকরণ সম্পর্কে নয়। কাজেই আধুনিক প্রক্রিয়া সমৃদ্ধ পরিবার পরিকল্পনা বা বন্ধ্যাকরণ জায়েয বলা যাবে না। বন্ধ্যাকরণ মূলতৎঃ আল্লহর সৃষ্টি পরিবর্তন করার অপরাধ। তা যে গুণাহের কাজ ও হারাম এবং তা আল্লাহর নিষিদ্ধ স্পষ্ট সন্তান হত্যার কাজ, তাতে কোনই সন্দেহ নেই। তবে কেউ চরম ঠেকায় পড়ে গেলে সেকথা স্বতন্ত্র।–অনুবাদক]
তা প্রয়োগ ব্যবহার করে কল্যাণের দিকটার সংরক্ষণ সম্ভব আর রাসূলে করীম (সা) তাই চেয়েছিলেন অর্থাৎ দুগ্ধপায়ী শিশুকে ক্ষতি থেকে বাঁচানো। আর দুগ্ধ সেবনকালে স্ত্রী সঙ্গম নিষিদ্ধকরণে যে বিপর্যয় ঘটার আশংকা, তা থেকেও তিনি উম্মতকে রক্ষা করতে চেয়েছেন।
এ আলোচনার আলোকে ইবনে হাম্বলের মতে ‘আযল’ জায়েয। তবে শর্ত হচ্ছে তার স্ত্রীর অনুমতিক্রমে হতে পারে। কেননা সঙ্গম স্বাদ ও তৃপ্তিলাভ এবং সন্তান এ উভয় দিকেই তার অধিকার রয়েছে। হযরত উমর (রা) স্ত্রীর অনুমতি ব্যতিরেকে ‘আযল’ করতে নিষেধ করেছেন।
এ থেকে ইসলামের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দৃষ্টিকোণ স্পষ্ট হয়ে উঠে। নবী করীম (সা) নারীদের অধিকারের ওপর সে সময়ই এতটা গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন, যখন দুনিয়ার মানুষ নারীর অধিকার বলতে কোন বস্তুর সাথে সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিল।
গর্ভপাত ঘটানো
ইসলাম গর্ভনিরোধক প্রতিক্রিয়া অবলম্বন করা জায়েয করেছে ঠিক সেই অবস্থায়, যখন তার প্রয়োজন তীব্র হয়ে দেখা দেয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও গর্ভের সঞ্চার হয়ে গেলে তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করা কোন অবস্থাতেই জায়েয নয়।
ফিকাহবিদগণ এ বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেন যে, ভ্রুণে প্রাণের সঞ্চার হয়ে যাওয়ার পর গর্ভপাত করান সম্পূর্ণ হারাম ও অপরাধ। একাজ কোন মুসলমানের জন্যেই জায়েয হতে পারে না। কেননা তা একটি জীবন্ত ও পূর্ণাঙ্গ সত্তার ওপর অমানুষিক জুলুম। এ কারণে ফিকাহবিদগণ বলেছেন, গর্ভপাত করান কালে যদি ভ্রুণ জীবন্ত প্রসূত হয়ে মরে যায় তাহলে ‘দিয়ত’- রক্তমূল্য-দিতে হবে। আর ভ্রূণ মৃত হলে জরিমানা দিতে হবে, যার পরিমাণ দিয়ত-এর অপেক্ষা কম হবে। কিন্তু তাঁরা বলেন, ভ্রূণকে বাঁচাতে গেলে মা’র জীবন নিঃশেষ হয়ে যাবে এবং গর্ভপাত করান ছাড়া প্রাণ বাঁচানর আর কোন উপায় নেই- তা যদি নির্ভরযোগ্য উপায়ে জানা যায়, তাহলে তখন গর্ভপাত করান জরুরী হয়ে পড়ে। শরীয়তের সাধারণ নিয়ম হচ্ছে, দুটো ক্ষতিকর ব্যাপারের দৃষ্টিতে প্রসূতির প্রাণ বাঁচানর জন্যে মা’র জীবনকে বিপদে নিক্ষেপ করা যায় না। যেহেতু মা’র জীবনই হলো আসল। তার অধিকারই অগ্রগণ্য। অতএব ভ্রুণের জীবন রক্ষার জন্যে মার জীবন কুরবান করা কিছুতেই বাঞ্ছনীয় হতে পারে না।
ইমাম গাজ্জালী বলেছেনঃ
গর্ভ নিরোধ ও গর্ভপাত- এ দুটোর মধ্যে পার্থক্য করতে হবে। গর্ভ নিরোধ সন্তান হত্যার সমান কাজ নয়। কেননা সন্তান হত্যা বলা যাবে তখন যখন গর্ভে সন্তানের অস্তিত্ব লাভ করবে। গর্ভে সন্তানের অস্তিত্ব লাভের কয়েকটি পর্যায় রয়েছে। প্রথম পর্যায় হচ্ছে, জরায়ুতে শুক্রকীটের স্থিতি লাভ এবং তাতে প্রাণ বা জীবন গ্রহণের যোগ্যতা হওয়া। এরূপ অবস্থায় তা বিনষ্ট করা গুনাহের কাজ। আর তাতে রূহ ফুঁকা হয়ে গেলে এবং সুস্থ পূর্ণাঙ্গ সম্পন্ন হয়ে উঠলে তখন তা বিনষ্ট করা অধিক মাত্রায় গুণাহের কারণ। আর চূড়ান্ত মাত্রার গুনাহ হচ্ছে, শিশুর জন্মের পর তাকে হত্যা করা।
(কিন্তু ইমাম গাজ্জালী একথা কি করে ভুলে গেলেন যে, শুক্রকীট বিনষ্ট করণও নিশ্চয়ই গুণাহ্ এবং তা জায়েয করা হলে দুনিয়ায় মানুষ সৃষ্টির আল্লাহর ইচ্ছাকেই সম্পূর্ণ ব্যর্থ করে দেয়া যেতে পারে, আর তা কখনই জায়েয হতে পারে না। বর্তমানে সেই পন্থাই উদ্ভাবিত ও ব্যাপকভাবে অবলম্বিত হচ্ছে। মূলত পুরুষ দেহ থেকে নির্গত শুক্রকীটই হচ্ছে পুরুষের সন্তান, যা হত্যা করতে কুরআন মজীদে বার বার নিষেধ করা হয়েছে। আর তা খাদ্যাভাবের আশংকায় হলে তো এ হারাম অত্যন্ত তীব্র হয়ে যাবে।)-আনুবাদক।
স্বামী-স্ত্রীর সামাজিক অধিকার
বিবাহ একটা সুসংবদ্ধ বন্ধন, একটা সুদৃঢ় প্রতিশ্রুতি। পুরুষ ও নারীর মাঝে সুদৃঢ় বন্ধন গড়ে তোলার জন্যেই আল্লাহ্ তা’আলা এ ব্যবস্থা কার্যকর করেছেন। বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর উভয়ই উভয়ের জুড়ি। ব্যক্তিত্বের দিক দিয়ে স্বতন্ত্র হলেও বাস্তবতার দৃষ্টিতে তারা একে অপরের জুড়ি। একজন অপরজনের প্রতিভু। প্রত্যেকেরই নিজস্ব কামনা-বাসনা ও আশা-আকাঙ্ক্ষা পরস্পর সম্পৃক্ত, সংযোজিত।
স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার এ সম্পর্কের চূড়ান্ত দৃঢ়তা ও অবিচ্ছিন্নতার কথা বোঝাবার উদ্দেশ্যেই কুরআন মজীদে বলা হয়েছেঃ (আরবী****************)
স্ত্রীরা তোমাদের পোশাক, তোমরা তাদের জন্যে পোশাক।
এ আয়াতের আসল বক্তব্য হচ্ছে, স্বামী-স্ত্রীকে পরস্পর সুসংবদ্ধ, পরস্পরের গোপনীয়তা আচ্ছাদনকারী, পরস্পরের সমর্থক-সাহায্যকারী এবং একজন অপরজনের জন্যে সৌন্দর্য বিধায়ক হতে হবে। অন্য কথায় প্রত্যেকেরই অপরজনের ওপর অধিকার রয়েছে। সে অধিকার পুরামাত্রায় অবশ্যই আদায় করতে হবে। এ অধিকার সম্পূর্ণ সমান, পুরুষদের প্রকৃতি অনুযায়ী তাদের দেয়া বিশেষ বিশেষ অধিকার ছাড়া আল্লাহর কথা থেকেই তা স্পষ্ট। তিনি বলেনঃ (আরবী****************)
স্ত্রীদের জন্যে রয়েছে সেসব যা আছে তাদের ওপর সুস্পষ্ট ও প্রচলিত বা সাধারণ নিয়মে। তবে পুরুষদের জন্যে তাদের ওপর একটা অগ্রাধিকার রয়েছে।
সে অগ্রাধিকারের পর্যায় হচ্ছে পরিচালক নিয়ন্ত্রক দায়িত্বশীল ও জবাবদিহি করতে বাধ্য হওয়ার। নবী করীম (সা)-কে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেনঃ আমাদের ওপর আমাদের স্ত্রীদের কি অধিকার রয়েছে? জবাবে তিনি বললেনঃ (আরবী****************)
তা হচ্ছে, তাদের নিজেদের সঙ্গে খাওয়াবে, নিজেদের মতোই পরাবে। আর মুখমণ্ডলের ওপর মারবে না, তাকে খারাপ-অশ্লীল গালাগালি করবে না এবং তাকে তার ঘর ছাড়া অন্য কোথাও ছাড়বে না। (আবূ দাঊদ, ইবনে হাব্বান)
কাজেই নিজ স্ত্রীর ভরণ-পোষণের ব্যাপরে ঔদাসিন্য বা উপেক্ষা দেখান কোন মুসলমানের পক্ষেই জায়েয নয়। হাদীসে বলা হয়েছেঃ (আরবী****************)
একজন লোকের গুনাহগার হওয়ার জন্যে এতটুকুই যথেষ্ট যে, যাদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব তার ওপর অর্পিত, তাদের প্রতি সে ব্যাপারে চরম উপেক্ষা দেখাবে। (আবূ দাঊদ, নিসায়ী, হাফেম)
স্ত্রীর মুখের ওপর মারার কোন অনুমতি ইসলাম দেয়নি। কেননা এ কাজ মানবীয় সম্মান ও মর্যাদা পরিপন্থী। তাতে দেহের সর্বাধিক সম্মানার্হ ও মর্যাদাসম্পন্ন অঙ্গ- দেহের সমস্ত সৌন্দর্য যেখানে কেন্দ্রীভূত- আহত ও ক্ষুণ্ণ হয়। নাফরমান ও স্বেচ্ছাচারী স্ত্রীকে প্রয়োজন মতো সুশিক্ষাদান ও গড়ে তোলার প্রশ্নে কখনও স্ত্রীকে হালকাভাবে মারাও যেতে পারে। কিন্তু তাকে কষ্ট দেয়া ও মুখমণ্ডলকে ক্ষতবিক্ষত করার মতো মারা কিছুতেই জায়েয হতে পারে না। স্ত্রীকে গালাগালি করাও জায়েয নয়। তার মনে কষ্ট দেয়া, তার জন্যে অসহনীয় কথাবার্তা বলা এমন কি তার জন্যে বদ দো’আ করা প্রভৃতিও সম্পূর্ণ নাজায়েয।
স্ত্রীর ওপর স্বামীর অধিকার পর্যায়ে নিম্নোদ্ধৃত হাদীসটি উল্লেখ্য। নবী করীম (সা) বলেছেনঃ (আরবী****************)
যে স্ত্রীলোক আল্লাহর প্রতি ঈমানদার, তার পক্ষে তার স্বামীর ঘরে এমন ব্যক্তিকে আসবার অনুমতি দেয়া বৈধ নয়, যাকে তার স্বামী পছন্দ করে না। স্বামীর অনুমতি ব্যতীত ঘরের বাইরে যাওয়াও তার জন্যে জায়েয নয়। এ ব্যাপারে অপর কারো কথা মান্য করাও তার উচিত নয়, স্বামীর শয্যা থেকে দূরে থাকাও নয় বাঞ্ছনীয়। স্বামী যদি অত্যাচারী হয়, তা হলে তাকে সন্তুষ্ট রাখার জন্যে সাধ্যমত চেষ্টা চালাবে। তার এই খিদমত স্বামী গ্রহণ করলে তো ভালই। আল্লাহ্ তার ওযর কবুল করে নেবেন এবং তার সত্যপন্থী হওয়াটাও প্রকাশ করে দেবেন। আর স্বামী যদি রাজি না হয়, তাহলে আল্লাহর কাছে তার অক্ষমতার ওযর পৌঁছে যাবে।
স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক ধৈর্য ধারণ
মুসলিম স্বামী মাত্রেরই কর্তব্য তার স্ত্রীর ব্যাপারে ধৈর্য ধারণ করা। বিশেষ করে তার মধ্যে এমন কিছু লক্ষ্য করে যা তার পছন্দ নয়। মানুষের মধ্যে মানুষ হওয়ার কারণে যে সব দোষত্রুটি স্বাভাবিক ভাবেই থাকে আর স্ত্রীলোকদের মধ্যে নারীত্বজনিত যে সব দুর্বলতা লক্ষ্য করা যায়, তা সহ্য করে নিতে অভ্যস্ত হওয়া স্বামীর একান্তই কর্তব্য। অনুরূপভাবে স্ত্রীর দোষগুলোর তুলনায় তার গুণগুলো এবং ত্রুটি-বিচ্যুতি অপেক্ষা ভাল ভাল দিকগুলোর প্রতিই নজর প্রকট করে রাখা বাঞ্ছনীয়। হাদীসে বলা হয়েছেঃ (আরবী****************)
কোন ঈমানদার পুরুষ যেন কোন ঈমানদার নারীকে ঘৃণা না করে। কেননা তার মধ্যে একটি ব্যাপার যদি অপছন্দনীয় থকে তাহলে অপরাপর গুণাবলী নিশ্চয়ই পছন্দনীয় পাওয়া যাবে। (মুসলিম)
আর আল্লাহ তা’আলা ইরশাদ করেছেনঃ (আরবী****************)
তোমরা স্ত্রীদের সাথে ভালভাবে বসবাস ও জীবন যাপন কর (ভাল আচরণ গ্রহণ কর)। তোমরা যদি তাদের অপছন্দ কর, তাহলে অসম্ভব নয় যে আল্লাহ্ তাদের মধ্যে অনেক কিছুই ভাল ও কল্যাণ জমা করে রেখেছেন।
ইসলাম যেভাবে স্বামীকে স্ত্রীদের অপছন্দনীয় ব্যাপারাদিতে ধৈর্য ধারণ করতে ও পরম সহিষ্ণুতা দেখাতে বলেছে, অনুরূপভাবে স্ত্রীদেরও নির্দেশ দিয়েছে নিজ নিজ স্বামীকে যথাসাধ্য সন্তুষ্ট রাখার জন্যে চেষ্টা চালিয়ে যেতে এবং স্বামীকে অসন্তুষ্ট রেখে রাত যাপন না করতে। হাদীসে বলা হয়েছেঃ (আরবী****************)
তিন ব্যক্তির নামায তাদের মাথার এক বিগত উপরেও যায় না। এক ব্যক্তি সে, যে লোকদের ইমামতি করে অথচ সেই লোকেরা তাকে পছন্দ করে না। দ্বিতীয় সেই স্ত্রীলোক, যে স্বামীকে অসন্তুষ্ট অবস্থায় রেখে রাত যাপন করে। আর তৃতীয় এমন দুই ভাই যারা পরস্পরের সাথে লড়াই-ঝগড়ায় লিপ্ত। (ইবনে মাযাহ, ইবনে হাব্বান)।
স্বামী-স্ত্রীর বিরোধ দেখা দিলে
পুরুষ ঘর ও পরিবারের কর্তা, পরিচালক ও নিয়ন্ত্রক। তাকে এ উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করা হয়েছে এবং তার মধ্যেই এর যোগ্যতা পাওয়া যায় বিধায় জীবন সংগ্রাম ক্ষেত্রে তার মর্যাদাও এরূপই বলে এবং মোহরানা ও খরচাদি বহনের দায়িত্ব তারই বলে এ মর্যাদায় তাকে অধিষ্ঠিত করা হয়েছে। অতএব তার আনুগত্য না করা ও আনুগত্য-বহির্ভূত কাজ করা, তার অবাধ্য হওয়া এবং তাকে ডিঙিয়ে যাওয়ার কোন অধিকার স্ত্রীর থাকতে পারে না। এরূপ যদি করা হয়ই তাহলে পারস্পরিক সম্পর্ক খুব খারাপ হয়ে যাওয়া অবধারিত। সংসার তরণী হাবুডুবু খাবে এবং কোন প্রকৃত মাঝির অনুপস্থিতির কারণে তা সম্পূর্ণরূপে নিমজ্জিত হয়ে যাওয়াও অসম্ভব নয়।
স্বামী যখন লক্ষ্য করবে যে, স্ত্রীর পক্ষ থেকে তাকে অমান্য করা হচ্ছে, স্ত্রী তার বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করে চলছে, তখন ভাল ভাল উপদেশ, যুক্তিপূর্ণ প্রাণস্পর্শী কথাবার্তা দ্বারা তাকে সংশোধন করার সাধ্যমত চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালাতে হবে। কিন্তু উপদেশ কার্যকর না হলে তাকে তার শয্যায় পরিহার ও বর্জন করতে হবে, যেন তার মধ্যে নারীসুলভ ভাবধার জাগ্রত হয় এবং শেষ পর্যন্ত আত্মসমর্পণ করে ও বাধ্য-অনুগত হয়ে যায়।
এ ব্যবস্থাপনা কার্যকর না হলে তার ওপর হাত তোলা যেতে পারে। কিন্তু তাই বলে চরম মাত্রার মারধোর, নিপীড়ন ও মুখের ওপর আঘাত করা কিছুতেই চলবে না, তা সম্পূর্ণ পরিহার করতে হবেই। কোন কোন স্ত্রীলোকের জন্যে হালকা ধরনের মারধোর অনেকটা কল্যাণকর ও সঞ্জীবক হয়ে দেখা দেয়। মারধোর অর্থ চাবুক বা ডান্ডা বা লাঠি দ্বারা মার নয়। নবী করীম (সা)-এর একটি উক্তি থেকে এ বিয়য়ে সুস্পষ্ট আলো পাওয়া যায়। তাঁর কোন খাদেম কোন ব্যাপারে তাঁকে রাগিয়েছিল কোন বিশেষ কাজের জন্যে। তখন তিনি বলেছিলেনঃ (আরবী****************)
কিয়ামতের দিন বদলা নেয়ার ব্যবস্থা না থাকলে আমি তোমাকে এ মিসওয়াক দ্বারাই আঘাত দিতাম। (তাবকাতে ইবনে সা’আদ)
মারধোর করাটা রাসূলে করীম (সা) আদৌ পছন্দ করেন নি। তিনি বলেছেনঃ (আরবী****************)
তোমাদের এক একজন নিজ স্ত্রীকে এমনভাবে মারধোর করে কেন, যেমন মনিব তার দাসকে মারছে? আর তারপরই সম্ভবত রাত্রিকালেই সে তার সাথে সঙ্গম করবে। (মুসনাদে আহমদ)
যারা স্ত্রীলোকদের মারধোর করে তাদের সম্পর্কে নবী করীম (সা) বলেছেনঃ (আরবী****************)
এ ধরনের লোক তোমাদের মধ্যে কখনও ভাল লোক বলে গণ্য হতে পারে না।
হাফেয ইবনুল হাজার লিখেছেনঃ
তোমাদের মধ্যে যারা ভাল লোক তারা কখনও নিজেদের স্ত্রীদের মারধোর করবে না রাসূলে করীম (সা)-এর এ কথা থেকে বোঝা যায় যে, স্ত্রীদের মারা মোটামুটি জায়েয বটে। তবে তার সঠিক সময় হচ্ছে তখন, যখন স্বামী তার স্ত্রীর মধ্যে যে ব্যাপারে তার আনুগত্য করা কর্তব্য সেই ব্যাপারেই আবাধ্যতা দেখতে পায়। এরূপ অবস্থায় সে তাকে বাধ্য ও আনুগত্য চাপানর উদ্দেশ্যে মারতে পারে। তবে যদি ধমক-ভীতি প্রদর্শন ইত্যাদির দ্বারা কাজ চলে যায়, তহলে মারপিট অবশ্যই পরিহার করতে হবে। কেননা তাতে স্ত্রীর মনে স্বামীর প্রতি ঘৃণা তীব্র হয়ে উঠে। আর তা সম্প্রীতিপূর্ণ দাম্পত্য জীবনের পরিপন্থী। অথচ বিবাহিত জীবনের তা-ই হচ্ছে আসল লক্ষ্য কিন্তু আল্লাহর নাফরমানী সংক্রান্ত্র কোন ব্যাপারে যদি তাকে মারতে হয় তবে তা স্বতন্ত্র কথা।
নাসায়ী গ্রন্থে হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেছেনঃ (আরবী****************)
রাসূলে করীম (সা) তাঁর কোন বেগমকে কিংবা কোন খাদেমকে কখনই মারেন নি। অপর কাউকেও তিনি কখনও মারবার জন্যে হাত তোলেন নি। তবেত আল্লাহর পথে কিংবা আল্লাহর মর্যাদার অমর্যাদাকরণের দরুন আল্লাহরই ওয়াস্তে কাউকে শাস্তি দিয়ে থাকলে সে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যাপার। (ফাতহুলবরী ৯ খণ্ড, পৃ. ২৪৯)
কিন্তু এসব পদক্ষেপও যদি ব্যর্থ হয় ও আ-ফলপ্রসু হয়ে যায় এবং পারস্পরিক বিরোধ বৈষম্য বিস্তীর্ণ ও গভীরতর হয়ে পড়ার আশংকা দেখা দেয়, তাহলে তখনই ইসলামী সমাজের প্রভাবশালী কর্তৃত্বসম্পন্ন ও কল্যাণকামী লোকেরা তাতে হস্তক্ষেপ করে সংশোধনের জন্যে চেষ্টা চালাবে। তার পন্থা হচ্ছে, স্বামীর পক্ষ থেকে একজন ও স্ত্রীর পক্ষ থেকে একজন সালিশকারী নিয়োগ করতে হবে, যার বাস্তবিকই উভয়ের কল্যাণকামী হবে। তারা স্বামী-স্ত্রীকে মিলিত করতে ও যে বিরোধ দেখা দিয়েছে তা দূর করতে চেষ্টা করবে, তা হলে আল্লাহ্ নিশ্চয়ই তাদের মধ্যে মিলমিশ সৃষ্টি করে দেবেন। এসব ব্যাপারে মহান আল্লাহর ঘোষণা হচ্ছেঃ (আরবী****************)
যে সব স্ত্রী সম্পর্কে তোমরা বিদ্রোহ ও অবাধ্যতার আশংকা বোধ করবে, তাদের বোঝও- উপদেশ দাও। তোমাদের শয্যায় তাদের ত্যাগ কর এবং তাদের মার। পরে যদি তারা তোমাদের আনুগত্য করে, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে তোমরা দোষ তালাস করে বেড়িও না। নিশ্চিত জানবে আল্লাহ্ উচ্চতর ও বড়ই মহান। আর তোমাদের পরস্পরের বিচ্ছেদের আশংকা দেখা দিলে স্বামীর আত্মীয়ের মধ্য থেকে একজন ও স্ত্রীর আত্মীয়দের মধ্য থেকে একজন সালিশ নিযুক্ত কর। এরা দুজন যদি বস্তবিকই সংশোধনের চেষ্টা প্রচেষ্টা চালায়, তাহলে আল্লাহ্ তাদের মধ্যে সামঞ্জস্য সৃষ্টি করে দেবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ ও সর্ববিষয়ে অবহিত।
কেবল এরূপ অবস্থায়ই তালাক দেয়া যেতে পারে
উপরে উল্লেখিত ও বিশ্লেষণকৃত সমস্ত চেষ্টা-প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেলে তারপরই প্রয়োজনের খাতিরে সর্বশেষ উপায় হিসেবে ইসলামী শরীয়ত প্রদত্ত পন্থা গ্রহণ করা স্বামীর জন্যে জায়েয হতে পারে, যেন সকল সমস্যা ও জটিলতা দূর হয়ে যায়, আর তা হচ্ছে তালাক দেয়া। ইসলাম খুব অনাগ্রহ ও অসন্তুষ্টি ভিত্তিতে এ পন্থা গ্রহণের অনুমতি দিয়েছে। তা তার কাছে পছন্দনীয় কাজ নয়, ওয়াজিব-ফরয নয়। নবী করীম (সা) বলেছেনঃ (আরবী****************)
আল্লাহর কাছে হালাল কার্যাবলীর মধ্যে সবচাইতে অধিক ঘৃণিত ও অপছন্দনীয় হচ্ছে তালাক।
(আরবী****************)
আল্লাহ্ তালাকের অপেক্ষা অধিক কোন না-পছন্দনীয় কাজকে হালাল করেন নি।
আর তালাক যে হালাল অথচ অপছন্দনীয় কাজ, তা এ কথায় স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, তালাক হচ্ছে একটি অনুমতি, কেবলমাত্র কঠিন প্রয়োজন ও উপায়হীন অবস্থায়ই তা প্রয়োগ করা জায়েয। পারিবারিক জীবন যখন অচল ও বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে, স্বামী-স্ত্রীর মনে পারস্পরের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ যখন তীব্র হয়ে উঠে এবং তাদের আল্লাহ্ নির্ধারিত সীমার মধ্যে টিকে থাকা সম্ভবপর না থাকে, পারস্পরিক দাম্পত্য অধিকারও আদায় করতে না পারে, তাহলে এ পন্থা গ্রহণ ব্যতীত কোন উপায়ই থাকে না। মিলের যখন কোন উপায়ই নেই তখন বেমিলই ভাল- এ একটি সাধারণ কথা। আল্লাহ্ বলেছেনঃ (আরবী****************)
তারা দুজন যদি পরস্পর বিছিন্ন হয়ে যায়, তাহলে আল্লাহ্ তাদের দুজনকেই স্বীয় প্রশস্ততার দ্বারা পরস্পর অ-বিমুখ ও অ-নির্ভরশীল বানিয়ে দেবেন।
ইসলামের পূর্বে তালাক প্রথা
তালাক কেবল ইসলাম প্রবর্তিত ব্যবস্থাই নয়। ইসলামের পূর্বে সমগ্র দুনিয়ায় তালাক ব্যবস্থার প্রচলন ছিল ব্যাপকভাবে। দু একটি জাতির ক্ষেত্রে অবশ্য ব্যতিক্রম দেখা যেত। স্বামী যখন স্ত্রীর ওপর রাগান্বিত হতো- কোন সঙ্গত কারণে কিংবা অসঙ্গতভাবেই, তাহলে তখন তাকে ঘর থেকে বহিষ্কৃত করত। স্ত্রী তখন স্বীয় প্রতিরক্ষা বা আত্মপক্ষ সমর্থনে কিছুই বলতে বা করতে পারত না। স্বামীর কাছ থেকে কোনরূপ বিনিময় লাভ করাও তার পক্ষে সম্ভবপর হতো না। অন্য কোন প্রকারের অধিকারও স্বীকৃত ছিল না। গ্রীকদের খ্যাতি ও প্রাধানের যুগে তাদের সভ্যতার বিজয় পতাকা যখন পতপত করে উড়ত তখন তাদের সমাজেও তালাক প্রথা কোনরূপ শর্ত বা বাধা বন্ধন ব্যতীতই কার্যকর ছিল। রোমানদের সমাজে বিয়ে অনুষ্টিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তালাক গণ্য হতো। এমনকি স্বামী-স্ত্রী তালাকহীনতার শর্ত আরোপ করলেও বিচারক বিয়ে বাতিল হয়ে যাওয়ার রায় দিয়ে দিত।
রোমানদের প্রাচীন গোত্র সমূহের মতে ধর্মীয় বিয়ের ক্ষেত্রে তালাক হারাম হয়ে যেত। তবে স্বামী তার স্ত্রীর ওপর সীমাহীন কর্তৃত্ব লাভ করত। এমনকি কোন কোন অবস্থায় স্ত্রীকে হত্যা করাও তার জন্যে বৈধ হয়ে যেত। উত্তরকালে তাদের ধর্মে তালাককে নাগরিক আইনের মতোই বৈধ ঘোষণা করা হয়।
ইয়াহূদী ধর্মে তালাক
ইয়াহূদী ধর্মে স্ত্রীদের মান-মর্যাদা উন্নত করতে চেষ্টা করা হয় বটে কিন্তু তালাককে বৈধ ঘোষণা করে তার বৈধতায় বিপুল প্রশস্ততা এনে দেয়া হয়। স্ত্রীর গুনাহের অপরাধ প্রমাণিত হয়ে যাওয়ার পর স্বামী ধর্মীয় দৃষ্টিতেই তালাক দিতে বাধ্য হয়ে যেত। স্বামী তার গুনাহ ক্ষমা করে দিলেও তাকে তালাক দেয়া তার জন্যে অপরিহার্য কর্তব্য হয়ে পড়ত। দশ বছর কাল অতিক্রান্ত হওয়ার পরও স্ত্রীর গর্ভে সন্তান জন্ম না নিলে আইনের দৃষ্টিতেই তালাক দেয়া জরুরী বিবেচিত হতো।
খ্রিস্ট ধর্মে তালাক
খ্রিস্ট ধর্ম তালাকের ব্যাপারে সম্পূর্ণ বিরোধিতা করেছে। একদিকে তা ইয়াহূদী ধর্মের বিরোধীতা করেছে। ইনজীল হযরত ইসার নামে তালাকদান কাজটিকে সম্পূর্ণ হারাম ঘোষণা করেছে। উপরন্তু তালাকদাতা পুরুষ ও তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর বিয়েকেও হারাম করে দিয়েছে। ইনজীল মথির বিবরণে বলা হয়েছেঃ
আর উক্ত হইয়াছিল, ‘যে কেহ আপন স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে, সে তাহাকে ত্যাগপত্র (তালাকনামা) দিউক। কিন্তু আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, যে কেহ ব্যভিচার ভিন্ন অন্য কারণে আপন স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে, সে তাহাকে ব্যভিচারিণী করে এবং যে ব্যক্তি সেই পরিত্যক্ত স্ত্রীকে বিবাহ করে, সে ব্যভিচার করে। (মথি-৫ অধ্যায়, ৩১-৩২ স্তোত্র)
মার্ক লিখিত সুসমাচারে বলা হয়েছেঃ
যে কেহ আপন স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া আমাকে বিবাহ করে, সে তাহার বিরুদ্ধে ব্যভিচার করে, আর যদি আপন স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়া আর একজনকে বিবাহ করেম তবে সেও ব্যভিচার করে।
বাইবেলে এই হারাম করণের কারণস্বরূপ বলা হয়েছেঃ
ইশ্বর যাহার যোগ করিয়া দিয়াছেন, মনুষ্য তাহার বিয়োগ না করুক। (মথি-১৯ অধ্যায়, ৬ স্তোত্র)
এই উক্তিটি স্বতঃই সত্য ও সঠিক। কিন্তু তালাক দেয়াকে হারাম ঘোষণার ক্ষেত্রে এ উক্তির প্রয়োগ বড়ই বিস্ময়কর। আল্লাহর পক্ষ থেকে স্বামী-স্ত্রীকে জুড়ে দেয়ার সহজ সরল অর্থ হচ্ছে, তিনি বিয়ে করার অনুমতি দিয়েছেন। বিয়েকে তালাক দেয়ার অনুমতি দিয়ে থাকেন তবে এ বিচ্ছেদও আল্লাহরই পক্ষ থেকে হয়েছে মনে করতে হবে- যদিও বিচ্ছিন্নকরণের কার্যটি মানুষ দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ থেকে স্পষ্ট হচ্ছে, আল্লাহ্ যাকে জুড়ে দিয়েছেন তাকে বিচ্ছিন্নকারী মানুষ নয়, সেই আল্লাহই।
ব্যভিচার সঙ্ঘটিত হলে উভয়কে বিচ্ছিন্নকারী কি আল্লাহ্ নন? ব্যভিচার ছাড়া বিচ্ছিন্ন করণের কারণ আরও আছে কি?
তালাকের ব্যাপারে খ্রিস্ট ধর্মের ভিন্নমত
ইনজীল যদিও ব্যভিচার সঙ্ঘটিত হলে স্ত্রীকে তালাক দেয়া হারাম বলে না, হারাম থেকে মুক্ত ও ব্যতিক্রম করে; কিন্তু ক্যাথলিক ধর্মম এ ব্যতিক্রমের ব্যাখ্যা দিয়েছে। তারা বলে, মূলত এখানে ব্যতিক্রম (exception) কিছুই নেই। তালাক দেয়ার কোন সুযোগই কোথাও নেই। খৃষ্ট ধর্মে তালাকের কোন অস্তত্বই স্বীকৃত নয়। তবে ব্যভিচার সঙ্ঘটিত হওয়ার কারণে তালাকের ব্যাপারটির সঠিক অর্থ হচ্ছে, ব্যভিচার নিজেই বিবাহ-বন্ধনকে ছিন্ন করে দেয়। এ কারণেই ব্যভিচার সঙ্ঘটিত হলে স্বামীর কর্তব্যই হচ্ছে স্ত্রীকে পরিত্যাগ করা।
প্রোটেস্টান্ট ধর্মমত এর সম্পূর্ণ বিপরীত রায় দিয়েছে। এ মতের লোকেরা বিশেষ অবস্থায় তালাক দেয়া জায়েয মনে করে। আর তা হচ্ছে স্ত্রীর ব্যভিচার করা কিংবা স্বামীর বিশ্বাসভঙ্গ করা প্রভৃতি। তাদের এ মত কিন্তু ইনজীল মথির ঘোষিত নীতির অতিরিক্ত। কিন্তু এরূপ অবস্থায় ইনজীল তালাকদাতা পুরুষ ও তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর পুনরায় বিবাহিত হওয়াকে হারাম বলেছে।
অর্থোডক্স (orthodox) ধর্মমতের অনুসারী লোকেরা মিশরে অনুষ্ঠিত তাদের ধর্মসভায় স্ত্রীর ব্যভিচারকরণ ও অন্যান্য কারণে তাকে তালাক দেয়া জায়েয ঘোষণা করেছ। ক্রমাগতভাবে তিন বছর কাল পর্যন্ত স্ত্রীর বন্ধ্যা থাকা, সংক্রামক রোগ এবং মীমাংসার আশা নেই এমন ঝগড়া-বিবাদের দীর্ঘসূত্রিতা প্রভৃতি এসব কারণের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু এসব কারণ ইনজীলের ঘোষণার ওপর অতিরিক্ত। এ কারণেই এ ধর্মমতের সংরক্ষকরা অন্যদেরকে এসব কারণে তালাক দেয়া জায়েয হওয়ার মত মানিয়া নিতে পারেনি। আর এ কারণেই মিশরের খ্রিস্ট আদালতে জনৈক খ্রিস্ট স্ত্রীর স্বামীর দারিদ্রের কারণে পেশ করা তালাক প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করে দিয়েছিল। সেই সাথে এ মন্তব্য করেছিল যে, ধর্মের কোন কোন নেতা ও এ মজিলিসের সদস্যরা এমন সব কারণের ভিত্তিতে তালাক দেয়া জায়েয বলেছেন, যার কোন সনদই ইনজীলে নেই- এটা বড়ই আশ্চর্যের বিষয়।
তালাকের ব্যাপারে খ্রিস্ট ধর্মের অনুসৃত নীতির পরিণাম
তালাকের ব্যাপারে খ্রিস্ট ধর্মে প্রবর্তিত এসব নিয়ন্ত্রণ ও বাধ্যবাধকতার পরিণাম খুবই খারাপ হয়ে দেখা দিল। খ্রিস্ট ধর্মের অনুসারীরা নিজেদের ধর্মকে অস্বীকার করতে শুরু করে দিল। আল্লাহ্ যাকে জুড়েদিলেন, তারা তাকে বিচ্ছিন্ন করে দিল। খ্রিস্টান পাশ্চাত্য এমন সব নাগরিক আইন (Civil code) বানাল, যার ফলে তাদের এ বাধ্যবাধকতা এড়িয়ে যাওয়া সম্পূর্ণ আইনমম্মত হয়ে গেল। আমেরিকা ও অন্যান্য কয়েকটি দেশে তালাককে অবাধ ও সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাধীন কাজ বানিয়ে দেয়া হলো। কার্যত তারা ইনজীলেকেই চ্যালেঞ্জ করে বসল। তার ফল এই দেখা দিল যে, সাধারণ কার্যকারণেই লোকেরা তালাকের অস্ত্র প্রয়োগ করতে শুরু করে দিল। তার চূড়ান্ত পরিণতি স্বরূপ দাম্পত্য জীবন ও পরিবার ব্যবস্থায় যখন চরম বিপর্যয় দেখা দিল, তখন সে সমাজে সুধীদের মনে প্রশ্ন দেখা দিল যে, আমরা কোথায় যাচ্ছি? তালাক মামলার একজন প্রখ্যাত বিচারক বলতে বাধ্য হলেন যে, তাদের দেশ থেকে দাম্পত্য ও পারিবারিক জীবন শেষ হয়ে যেতে আর বড় দেরী নেই। অতঃপর নারী-পুরুষের মধ্যে চরম নৈরাজ্য ও অবাধ যৌন সম্পর্ক স্থাপিত হবে। এক্ষণে দাম্পত্য জীবন একটা ব্যবসায়ী কোম্পানীর অবস্থা পরিগ্রহ করে গেছে। তার দুজন অংশীদার যে কোন অতি সাধারণ ও নগণ্য কারণে পারস্পরিক চুক্তি ভঙ্গ করে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে। এ অবস্থা দুনিয়ার কোন ধর্ম মতেরই অনুকূল বা তার সাথে সামঞ্জস্যশীল নয়। কেননা এক্ষণে কোন ধর্মবিশ্বাস তাদের জুড়ে রাখতে পারছে না। নিছক যৌন সুখ-সম্ভোগই তাদের নারী পুরুষের সম্পর্কের একমাত্র ভিত্তি হয়ে দাড়াল।
তালাক পর্যায়ে খ্রিস্ট ধর্মের স্বতন্ত্র ভূমিকা
ধর্মের শিক্ষাকে বাদ দিয়ে পারিবারিক আইনকে নাগরিক বিধিতে রপান্তরিত করার দৃষ্টান্ত খ্রিস্টান পাশ্চাত্য ছাড়া আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। কেবলমাত্র খ্রিস্টানরাই এ ক্ষেত্রে ধর্মের শিক্ষাকে মারাত্মক হয়ে দেখা দেয়েছে। তার মূলে একটা কারণও প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছিল। তাদের নিজেদেরই এ ধারণা হয়ে গিয়েছিল যে, তালাক পর্যায়ে তাদের ধর্মের বিধিবিধান বাস্তবতার পরিপন্থী। মানব প্রকৃতি তার সাথে সামঞ্জস্য সম্পন্ন হয়। অতএব মানব জীবনে তার প্রয়োগ ঠিক নয়। (আরবী****************)
খ্রিস্ট ধর্মের শিক্ষা সাময়িক
তালাক পর্যায়ে ইনজীল কিতাবে যা কিছু বলা হয়েছে, তা যদি সঠিক ও যথার্থ হয়ও এবং প্রাথামিক যুগে তাতে কোনরূপ পরিবর্তন যদি সাধিত না-ও হয়ে থাকে, তবুও একথা স্পষ্ট যে, হযরত ঈসা (আ) কোন স্থায়ী চিরন্তন ও শাশ্বত বিধান দিয়ে যান নি। তা সর্বকালের সকল মানুষের জন্যে অনুসরণীয় ও গ্রহণযোগ্য নয়। ইয়াহূদীরা আল্লাহর দেয়া সুযোগ সুবিধা ও অনুমতির ক্ষেত্রে সীমালংঘন করে গিয়েছিল। তালাকের ক্ষেত্রে তাদের এ সীমালংঘন অত্যন্ত প্রকট। হযরত ঈসা তার বিরোধিতাই করতে চেয়েছিলেন মাত্র। মথি রচিত সুসমাচারে উদ্ধৃত হয়েছেঃ ফরাসীরা যখন হযরত ঈসার পরীক্ষা নিতে চেয়েছিল, তখন তারা তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলঃ
যে-সে কারণে কি আপন স্ত্রীকে পরিত্যাগ করা বিধেয়? তিনি উত্তর করিলেন, তোমরা কি পাঠ কর নাই যে, সৃষ্টিকর্তা আদিতে পুরুষ ও স্ত্রী করিয়া তাহাদিগকে নির্মাণ করিয়াছিলেন, আর বলিয়াছিলেনঃ এ কারণ মনুষ্য পিতা ও মাতাকে ত্যাগ করিয়া আপন স্ত্রীতে আসক্ত হইবে এবং সে দুজন একাঙ্গ হইবে? সুতরাং তাহারা আর দুই নয়, কিন্তু একাঙ্গ। অতএব ঈশ্বর যাহার যোগ করিয়া দিয়েছেন; মনুষ্য তাহার বিয়োগ না করুক। তাহারা তাহাকে কহিল, তবে মোশি কেন ত্যাগ পত্র দিয়া পরিত্যাগ করিবার বিধি দিয়াছেন? তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, তোমাদের অন্তকরণ কঠিন বলিয়া মোশি তোমাদিগকে আপন স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিবার অনুমতি দিয়াছিলেন, কিন্তু আদি হইতে এরূপ হয় নাই। আর আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, ব্যভিচার দোষ ব্যতিরেকে যে কেহ আপন স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যকে বিবাহ করে, সে ব্যভিচার করে এবং যে ব্যক্তি সেই পরিত্যক্তা স্ত্রীকে বিবাহ করে সেও ব্যভিচার করে। (মথি লিখিত সুসমাচার-১৯ অধ্যায়, ৩-৯ স্তোত্র)
এ থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, হযরত মূসা যে তালাকের অনুমতি দিয়েছিলেন, ইয়াহূদীরা তাতে যখন বাড়াবাড়ি করল, তখন হযরত মসীহ শাস্তি হিসেবে তাদের ওপর তালাককে হারাম করে দিলেন। কেবলমাত্র ব্যভিচারিণীর জন্যে তালাক থাকল। আর তা ছিল সাময়িক ব্যবস্থা। হযরত মুহাম্মাদ (সা)-এর আগমন ও সর্বাত্মক ও চিরন্তন শাশ্বত শরীয়তের প্রবর্তিত হওয়া পর্যন্তই ছিল তার আয়ুষ্কাল।
হযরত ঈসা মসীহ তালাকের এই বিধানকে চিরন্তন শরীয়তরূপে পেশ করতে চেয়েছিলেন, তা যুক্তিসঙ্গত কথা নয়। কেননা তার সঙ্গী সাথী হাওয়ারী ও শিষ্য শাগরিদরাই এই বিধানকে অচল ঘোষণা করে দিলেন। তাঁরা বলেছিলেনঃ যদি আপন স্ত্রীর সঙ্গে পুরুষের এরূপ সম্বন্ধ হয় তবে বিবাহ করা ভাল নয়। (মথি সুসমাচার-১৯ অধ্যায়, ১০ স্তোত্র)
কেননা এরূপ অবস্থায় বিয়ে করা অর্থ নিজের গলায় এমন দড়ি বাধা যার থেকে মুক্তি লাভ কখনই সম্ভব নয়। পুরুষের হৃদয় স্ত্রীর দিক থেকে যতই ঘৃণাপূর্ণ ও বিদ্বেষী হোক-না-কেন এবং সে তার প্রতি যতই মনক্ষুণ্ণ হোক-না-কেন উভয়ের স্বভাব-মেজাজ ও ঝোঁক-প্রবণতায় যতই পার্থক্য থাকুক না কেন।
তালাকের ব্যাপারে ইসলামের নিয়ন্ত্রণ
তালাকের ক্ষেত্রে ইসলাম বিভিন্ন শর্ত ও নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেছে। ফলে সে ক্ষেত্রটি অত্যন্ত সংর্কীণ হয়ে গেছে। উপরে যে সব উপায়ের উল্লেখ আমরা করেছি সেগুলো ব্যবহার না করে এবং বিনা কারণে তালাক দেয়া ইসলামে সম্পূর্ণ হারাম ও নিষিদ্ধ। কেননা তা করা হলে শুধু স্ত্রীরই নয়, স্বামীরও খুবই ক্ষতি ও অসুবিধা হওয়া অনিবার্য। তা তার নিজের কল্যাণেরও পরীপন্থী। কাজেই এরূপ অবস্থায়স্ত্রীকে তালাক দেয়া তেমনি হারাম, যেমনি ধন-মাল বিনষ্ট করা হারাম। নবী করীম (সা) বলেছেনঃ (আরবী****************)
না নিজেকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে, না অন্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে বা তা হতে দেবে।
এই হাদীসের দৃষ্টিতেও বিনা কারণে অযথা তালাক দেয়া জায়েয নয়।
যারা আনন্দের আতিশয্যে খুব বেশি তালাক দেয় তাদের এ কাজ আল্লাহর পছন্দ নয়, রাসূলেরও নয়। নবী করীম (সা) ইরশাদ করেছেনঃ (আরবী****************)
স্বাদ আস্বাদন করে বেড়ানোর পুরুষ বা নারী আমার পছন্দ নয়।
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেনঃ (আরবী****************)
তালাক প্রয়োজনের কারণেই বিধিবদ্ধ করা হয়েছে।
হায়েয অবস্থায় তালাক দেয়া হারাম
তালাক দেয়ার প্রয়োজন দেখা দিলেই যে-কোন সময়ই তালাক দেয়া জায়েয নয়। তার জন্যে উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষা করা আবশ্যক। আর শরীয়তের দৃষ্টিতে তার জন্যে উপযুক্ত সময় হচ্ছে স্ত্রীর পবিত্র অবস্থা অর্থাৎ স্ত্রী যখন হায়েয নিফাসের অবস্থায় নয় এবং এমন পবিত্র অবস্থা, যখন তার সাথে সঙ্গম করেনি। তবে স্ত্রী গর্ভবতী হলে ও তার গর্ভ প্রকাশমান হয়ে পড়লে তখন ভিন্ন কথা।
এরূপ শর্ত এ জন্যে আরোপ করা হয়েছে যে, হায়েয বা নিফাস অবস্থায় স্বামী স্ত্রীর কাছ থেকে আলাদা থাকে। স্ত্রী সঙ্গম থেকে বঞ্চিত থাকতে বাধ্য হয়। এরূপ অবস্থায় স্বামী তার প্রতি মণক্ষুণ্ণ বা ক্ষুদ্ধ থাকতে পারে। আর এ কারণেই তাকে তালাক দিতে উদ্যত হয়ে থাকতে পারে। এই সম্ভবনার কারণে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, স্বামী তালাক দেয়ার জন্যে স্ত্রীর সম্পূর্ণ পবিত্র হওয়ার অপেক্ষায় থাকবে। আর পবিত্র হওয়ার পর সঙ্গম করার পূর্বেই তালাক দিয়ে দেবে।
স্ত্রীর হায়েয অবস্থায় তালাক দেয়া যেমন হারাম, অনুরূপভাবে যে পবিত্রাবস্থায় সঙ্গম করেছে, তখন তালাক দেয়াও হারাম। কেননা স্বামী যদি জানতে পারত যে স্ত্রী গর্ভবতী হয়েছে তাহলে সে হয়ত তাকে তালাক দিতই না। গর্ভ হওয়ার কারণে স্ত্রীকে তালাক না দেয়ার সিদ্ধান্ত করাও বিচিত্র নয়।
কিন্তু স্ত্রী যখন পবিত্রাবস্থায় হবে ও তখন স্বামী তার সাথে সঙ্গম করেনি অথবা স্ত্রী গর্ভবতী হয়েছে ও সে গর্ভ প্রকাশমান হয়ে পড়ছে, এরূপ অবস্থায় তালাক দেয়ার অর্থ, স্ত্রীর প্রতি ঘৃণা প্রচণ্ড রূপ ধারণ করেছে। কাজেই এরূপ অবস্থায় তালাক দেয়ার অনুমতি আছে।
হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা) নবী করীমের জীবদ্দশায় তাঁর স্ত্রীকে হায়েয অবস্থায় তালাক দিয়েছিলেন। হযরত উমন (রা) এ বিষয়ে নবী করীম (সা)-কে জিজ্ঞেস কররে তিনি বললেনঃ (আরবী****************)
তাকে বল, সে যেন স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়। পরে তার পবিত্রাবস্থায় ইচ্ছা করলে যেন তালাক দেয় সঙ্গমের পূর্বেই।
এ হচ্ছে ইদ্দতের জন্যে তালাক। আল্লাহ্ তা’আলা নিম্নোদ্ধৃত আয়াতে সেই কথাই বলেছেনঃ (আরবী****************)
হে নবী! তোমরা যখন স্ত্রীদের তালাক দেবে, তখন তালাক দেবে ইদ্দত পালনের লক্ষ্যে।
তার অর্থ ‘তুহর’- স্ত্রীর পবিত্রাবস্থায় তালাক দান।
অপর একটি হাদীসে রাসূলের কথাটি এ ভাষায় উদ্ধৃত হয়েছেঃ (আরবী****************)
তাকে বল, সে তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিক। পরে পবিত্রাবস্থায় বা গর্ভবতী অবস্থায় তাকে তালাক দিক।
তবে এখানে প্রশ্ন উঠে, ‘হায়েয’ অবস্থায় তালাক দিলে তা সঙ্ঘটিত হবে কিনা? সকলের সাধারণভাবে জানা কথা হচ্ছে তালাক যখনই দিক, তা সঙ্ঘটিত হবেই। কিন্তু অসময়ে তালাক দিলে দাতা গুনাহগার হবে।
কোন কোন ফিকাহবিদ বলেছেন, অসময়ে তালাক দিলে তা সঙ্ঘটিত হবে না। কেননা আল্লাহ্ তা’আলা এ ধরনের তালাক বিধিবদ্ধ করেন নি। তার অনুমতিও দেন নি। এ কারণে এ ধরনের তালাক শরীয়তসম্মত নয়। তাহলে সে তালাককে সহীহ বলা যায় কি করে আর তা কার্যকরই বা হবে কেমন করে?
হযরত ইবনে উমর (রা)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলঃ (আরবী****************)
যে লোক তার স্ত্রীকে ‘হায়েয’ অবস্থায় তালাক দিল, তার সম্পর্কে আপনার মত কি?...... উত্তরে তিনি প্রশ্নকারীকে তার নিজের স্ত্রীকে ‘হায়েয’ তালাক দেয়ার কাহিনী শোনালেন এবং বললেন, নবী করীম (সা) সে তালাক রদ করেছিলেন এবং তাকে তালাক গণ্যই করেন নি।
তালাকের কসম খাওয়া হারাম
‘তালাক’ কে কসম বানানো অর্থাৎ অমুক কাজ করা বা না করায় ‘তালাক হয়ে যাবে’ বলা জায়েয নয়। নিজের স্ত্রীকে ভয় দেখিয়ে বলা যে, তুই এ কাজ করলে তোকে তালাক- সম্পূর্ণ নাজায়েয। কেননা ইসলামে কসমের একটা বিশেষ ভাষা ও শব্দ আছে, তা ভিন্ন অপর কোন ভাষা বা শব্দে কসম কিরা অনুষ্টিত হয় না বা তা করার অনুমতি ইসলাম দেয়নি।
তা হচ্ছে আল্লাহর নামে কসম খাওয়া। রাসূলে করীম (সা) বলেছেনঃ (আরবী****************)
যে লোক আল্লাহর নাম ছাড়া অন্য কিছুর নামে কিরা করবে, সে শিরক করে।
(আরবী****************)
যে লোক কিরা বা কসম খাবে, সে যেন আল্লাহর নামে কিরা কসম করে, নতুবা যেন চুপ করে থাকে।
তালাকপ্রাপ্তা স্বামীর ঘরে ইদ্দত পালন করবে
ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীর কর্তব্য তার স্বামীর ঘরে ইদ্দত পালন করা- ইদ্দতকাল অতিবাহিত করা। সে ঘর ত্যাগ করে চলে যাওয়া- বাইরে বের হওয়া হারাম। স্বামীর পক্ষেও স্ত্রীকে ইদ্দতকালে তার ঘর থেকে বহিষ্কৃত করা হারাম। কেননা ইদ্দতকালে স্বামী স্ত্রীকে পুনরায় গ্রহণ করতে পারে, তার সম্ভাবনা রয়েছে- যদি সে এক বা দুই তালাক দিয়ে থাকে। এরূপ অবস্থায় যদি ঘরে স্বামীর কাছাকাছি থাকে, তাহলে স্বামীর ক্রোধ বা অসন্তোষ দূর করার সুযোগ পাবে। আর স্বামীও তার ব্যাপারে পুনর্বিবেচনা করার সুযোগ লাভ করবে।
গর্ভাধারের পবিত্রতার নিশ্চয়তা বিধান- গর্ভে সন্তান নেই, এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া, স্বামীর অধিকারের ওপর গুরুত্ব আরোপ এবং তার স্ত্রীত্বের মর্যাদা রক্ষার উদ্দেশ্যে ইদ্দত পালনের হুকুম দেয়া হয়েছে। মানব মনের অবস্থা পরিবর্তনশীল। পরিবর্তিত অবস্থায় মানুষের মনের অবস্থারও পরিবর্তন ঘটে, নতুন দৃষ্টিকোণে চিন্তা করে। ক্রোধ ও অসন্তোষ দূর হয়ে গিয়ে তথায় সন্তুষ্টি ও সম্প্রীতির উদ্রেক হওয়া কিছুমাত্র অস্বাভাবিক নয়। আবেগে প্রবাহিত মানুষ ঠাণ্ডা মন-মেজাজে চিন্তা করতে শুরু করে। আর তার ফলে যাকে পছন্দ নয়, তাকে পছন্দও করতে পারে। স্বামীর ঘরে ইদ্দত পালনের এ বাধ্যবাধকতার তাৎপর্য খুবই ব্যাপক ও গভীর।
তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা’আলা বলেছেনঃ (আরবী****************)
তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যিনি তোমাদের রব্ব। তোমারা তাদের ঘর থেকে তাদের বহিষ্কৃত করো না, তারাও যেন বের হয়ে না যায়। তবে সুস্পষ্ট প্রকাশ্য যে লোক আল্লাহর নির্দিষ্ট করা সীমা লংঘন করে, সে নিজেরই ওপর জুলুম করে। তোমরা তো জানো না, আল্লাহ্ হয়ত এর পর কোন নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব করবেন।
কিন্তু স্বামী-স্ত্রী বিছিন্ন করা যদি অপরিহার্যই হয়ে পড়ে, তা হলে দুজনের ভালভাবে ও প্রচলিত নিয়মে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া উচিত।
স্ত্রীকে কোনরূপ কষ্ট দেয়া চলবে না, মিথ্যা অভিযোগ তোলা বা দোষারোপ করা চলবে না, কারো অধিকারও হরণ করা যাবে না। আল্লাহ্ বলেছেনঃ (আরবী****************)
তাহলে ভালভাবেই তাদের রাখ অথবা ভালভাবেই তাদের বিছিন্ন করে দাও।
বলেছেনঃ (আরবী****************)
তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীদের প্রচলিত নিয়মে কিছু মালমাত্তা দিতে হবে। মুত্তাকী লোকদের ওপর এটা তাদের অধিকার এবং তা তাদের দায়িত্ব।
এক তালাকের পর আর এক তালাক
ইসলাম মুসলমানকে নিয়ম করে দিয়েছে যে, স্ত্রীকে সে তিন তালাক একবারে নয়, তিন তালাক ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দেবে। তার নিয়ম হচ্ছে, যে তুহরে- পবিত্রাবস্থায়- স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করে নি, তখন এক তালাক দেবে। আর তাকে এমনি অবস্থায়ই রেখে দেবে। এভাবে থাকার মধ্য দিয়ে তার ইদ্দতকাল নিঃশেষ হয়ে যাবে। ইদ্দতকালেই স্বামী যদি তাকে রাখার সিদ্ধান্ত করে, তাহলে অতি সহজেই তাকে ফিরিয়ে নিতে পারবে। কিন্তু যদি সে ফিরিয়ে না নেয়, আর এ অবস্থায়ই ইদ্দতকাল শেষ হয়ে যায়, তাহলে পরেও নতুন বিয়ের মাধ্যমে তাকে ফিরে পেতে পারবে। আর স্বামী যদি তাকে রাখার কোন প্রয়োজনই বোধ না করে, তাহলে তখন স্ত্রী আর একজনকে স্বামীত্বে বরণ করে নিতে পারবে।
প্রথমবারের তালাক দানের পর স্বামী যদি তাকে পুনরায় স্বীয় স্ত্রীত্বে ফিরিয়ে নেয়, পরে দুজনের সম্পর্ক আবার খারাপ হয়ে যায় ও মিলমিশ সৃষ্টির সব পথই রুদ্ধ হয়ে যায়, তাহলে সে দ্বিতীয়বারও তালাক দিতে পারে। এই যে পন্থার উল্লেখ করা হলো, এতে এখনও স্বামীর অধিকার অবশিষ্ট থাকে যে, ইদ্দত চালাকালে সে তাকে ফিরিয়ে নেবে কিংবা ইদ্দত শেষ হয়ে যাওয়ার পর নতুন আকদ করে তাকে স্ত্রীত্বে বরণ করে নেবে।
কিন্তু দ্বিতীয়বার ফিরায়ে গ্রহণ করার পর তৃতীয়বারও যদি তালাক দেয়, তাহলে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হবে যে, এ দুজনার মধ্যে ঘৃণা ও বিদ্বেষ এত তীব্র হয়ে উঠেছে যে, এদের মধ্যে মিলমিশ হওয়ার কোন আশাই নেই। এরূপ অবস্থায়- এই তৃতীয়বার তালাক দেয়ার পর স্বামী স্ত্রীকে আবার গ্রহণ করতে পারবে না। এক্ষণে সে তার জন্যে হালাল নয়, যতক্ষণ না সে অপর এক স্বামী গ্রহণ করে তার সাথে ঘর করছে। এ বিয়ে সহীহ হতে হবে, শরীয়ত মুতাবিক হতে হবে। বিয়ে লক্ষ্য হতে হবে, শুধু প্রাক্তন স্বামীর জেন্যে হালাল বানানর উদ্দেশ্যে বিয়ে হলে চলবে না।
তালাক দেয়ার এই হচ্ছে শরীয়তসম্মত নিয়ম ও পন্থা যদি কেউ এ পদ্ধতি ছাড়া অন্যভাবে- একই সময়ে এক এক করে তিন তালাক কিংবা এক বাক্যে তিন তালাক দেয়, তবে তা শরীয়ত প্রদত্ত নিয়ম ও পন্থার সম্পূর্ণ পরিপন্থী হবে। সে লোক হেদায়েতের পথ ত্যাগ করে গুমরাহীর পথ অবলম্বন করে চলেছে, সিরাতুল মুস্তাকীমকে সে হারিয়ে ফেলেছে। সহীহ্ হাদীসে বলা হয়েছে, রাসূলে করীম (সা) জানতে পারলেন, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে একসঙ্গে তিন তালাক দিয়েছেন। তিনি ক্রোধে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেনঃ ( আরবি******************)
আমি তোমাদের মধ্যে বর্তমান অবস্থায়ই এ লোকটি আল্লাহর কিতাব নিয়ে তামাসা খেলছে? এক ব্যক্তি এ সময় দাঁড়িয়ে বলল, ইয়া রাসূল! এমন ব্যক্তিকে কি আমি হত্যা করব না? (নিসায়ী)
স্বামী স্ত্রীকে তালাক দিলে ও নির্দিষ্ট ইদ্দতের মেয়াদ শেষ হয়ে এলে স্বামীর কর্তব্য দুটো কাজের মধ্যে যে কোন একটি করাঃ
হয় তাকে ভালভাবে ও প্রচলিত নিয়মে রেখে দেবে অর্থাৎ ভাল আচরণ ও ব্যবহার করার ও তাঁকে সংশোধন করে নেয়ার উদ্দেশ্যে ফিরিয়ে নিয়ে স্ত্রীত্বে বরণ করবে, লড়াই-ঝগড়া করার বা অকারণ কষ্ট দেয়ার কোন উদ্দেশ্য থাকবে না।
অথবা ভালভাবে ও প্রচলিত নিয়মে বিচ্ছিন্নতা অবলম্বন করবে অর্থাৎ ইদ্দত শেষ হয়ে যাওয়া পর্যন্ত তাকে ফেলে রাখাবে। তারপর কোনরূপ ক্ষতি সাধন না করেই- এবং তার সব অধিকার আদায় করেও তাতে কোনরূপ কার্পণ্য না করে তাকে বিদায় করে দেবে।
ইদ্দতের মেয়াদ শেষ হয়ে এলে স্ত্রীকে কষ্ট ও পীড়ন দেয়া ও ইদ্দতের মেয়াদ দীর্ঘ করার উদ্দেশ্যে তাকে ফিরিয়ে নেবে এবং দীর্ঘদিন পর্যন্ত দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ থেকে তাকে বঞ্চিত রাখাবে, স্বামীর জন্যে তা আদৌ জায়েয নয়।
জাহিলিয়াতের আমলে লোকেরা এরূপ আচরণ গ্রহণ করত। কিন্তু আল্লাহ্ তা’আলা এভাবে স্ত্রীকে কষ্ট দেয়াকে হারাম করে দিয়েছেন। তিনি এই হারাম করে দেয়ার কথা খুবই মর্মস্পর্শী ভঙ্গীতে বলেছেনঃ ( আরবি******************)
তোমরা যখন স্ত্রীদের তালাক দেবে,পরে তারা তাদের ইদ্দত শেষ করে দিল তখন ভালভাবে তাদের ফিরিয়ে রাখা অথবা ভালভাবে তাদের বিদায় করে দাও। কষ্ট দেয়ার উদ্দেশ্যে তাদের আটকে রাখবে না। তাহলে তা হবে সীমালংঘন। আর যে তা করবে, সে নিজেরই ওপর জুলুম করবে। আর আল্লাহর আয়াতসমূহকে হাস্যকর ঠাট্টা বিদ্রেূপর শিকার বানিও না। আর আল্লাহর অনুগ্রহকে- যা তোমাদের ওপর তিনি করেছেন স্মরণ কর। স্মরণ কর সেই কিতাব ও হিকমতকে যা তিনি তোমাদের জন্যে নাযিল করেছেন। তিনি তো তোমাদের উপদেশে দিচ্ছেন। তোমরা আল্লাহকে ভয় করে চলবে আর জেনে রাখবে, আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে পূর্ণ অবহিত। (সূরা বাকারাঃ ২৩১)
এ আয়াত কয়টি গভীর মনোনিবেশ সহকারে পাঠ করলে আমরা বুঝতে পারি, এখানে সাতটি বাক্যাংশ, তাতে ভয় প্রদর্শনের পর ভয় প্রদর্শন, সাবধান কারণের পর সাবধানকরণ রয়েছে। উপদেশ রয়েছে, নসীহতও রয়েছে। স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে আল্লাহর নিয়ামতসমূহ। সেই সাথে বারবার ভীতির বাণীও রয়েছে এতে। বস্তুত যার হৃদয় রয়েছে, মন দিয়ে লক্ষ্য করতে যে প্রস্তুত, যে সজাগ দৃষ্টি সম্পন্ন, তার জন্যে এ আয়াত কয়টি অতীব মূল্যবান।
তালাক প্রাপ্তকে ইচ্ছামত বিয়ে করতে বাধা দেবে না
তালাকপ্রাপ্তার ইদ্দতের মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে যাকে সে চাইবে, পছন্দ করবে, তাকে বিয়ে করতে তাকে বাধা দেয়া যাবে না। তার প্রাক্তন স্বামী বা তার অভিভাবক কিংবা অন্য কারোরই এ কাজ করার অধিকার নেই। শরীয়ত ও প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী প্রস্তাব দান ও নিজের মানুষের সন্তুষ্টির ভিত্তিতে বিয়ে হতে থাকলে তার ওপর আপত্তি করারও অধিকার নেই কারো। কোন কোন পুরুষ নিজ স্ত্রীকে তালাক দিয়েও তার ওপর স্বীয় কর্তৃত্ব বহাল রাখতে ও প্রভাব খাটাতে চেষ্টা করতে থাকে। অপর পুরুষ সম্পর্কে তাকে ভয় দেখাতে ও তার সাথে বিয়ে হলে ভাল হবে না বলে ধমকাতে থাকে। চরম মুর্খতা, বর্বরতা ও জাহিলিয়াতের চরিত্র ছাড়া এ আর কিছুই নয়।
অনুরূপভাবে স্ত্রী যদি তার প্রাক্তন স্বামীকে পুনর্বার বিয়ে করতে- স্বামীত্বে বরণ করতে ইচ্ছুক হয়, আর ভালভাবে ও প্রচলিত নিয়মে যাদি উভয়েই রাজি হয় ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, তাহলে অভিভাবক বা ঘরের অন্য কারোরই তাতে বাধার সৃষ্টি করা জায়েয নয়। আল্লাহ্ বলেছেনঃ সন্ধি সুলেহ করে নেয়াই কল্যাণকর।
বলেছেনঃ ( আরবি******************)
তোমরা যখন তোমাদের স্ত্রীদের তালাক দিয়ে দাও আর তারা ইদ্দতের মেয়াদ পূর্ণ করে ফেলে তখন তারা তাদের ভাবী স্বামীকে বিয়ে করবে- যদি তারা প্রচলিত নিয়মে বিবাহিত হতে পরস্পর রাজি হয়ে যায়- তাতে তোমরা বাধাদান বা অসুবিধা সৃষ্টি কর না। একথা বলে উপদেশ দেয়া হচ্ছে তাদের, যাদের ঈমান রয়েছে আল্লাহর প্রতি, পরকালের প্রতি। তোমাদের জন্যে এ অতীব পবিত্র পরিচ্ছন্ন নিষ্কলুষ পন্থা। আল্লহই জানেন, তোমরা জান না। (সূরা বাকারাহঃ ২৩২)
স্বামীর প্রতি ঘৃণা সম্পন্না স্ত্রীর অধিকার
কোন স্ত্রী যদি তার স্বামীর প্রতি ঘৃণা পোষণ করে, তাকে অপছন্দ করে এবং তার সাথে মিলেমিশে একাত্ম হয়ে ঘর-কন্না করতে পারবে বলে মনে করতে না পারে, তাহলে বিনিময় মূল্য দিয়ে সে তার নিজের আযাদী ও মুক্তি ক্রয় করতে পারে। স্বামী যে মোহরানা বা উপহার-উপঢৌকন তাকে দিয়েছে তা সব- কিংবা যতটায় উভয় পক্ষ রাজি হয় তা ফিরিয়ে দিয়ে নিজেকে স্ত্রীত্বের বন্ধন থেকে মুক্ত করতে পারে- এ অধিকার তার রয়েছে। তবে স্বামী তার জন্যে যা কিছু ব্যয় করেছে তার অধিক কিছু তার গ্রহণ করা উচিত নয়। আল্লাহ্ নিজেই বলেছেনঃ ( আরবি******************)
তোমরা যদি একথা চিন্তা করে ভয় পাও, স্বামী স্ত্রী দুজনে আল্লাহর নির্ধারিত সীমা রক্ষা করে চলতে পারবে না, তাহলে স্ত্রী যা-ই বিনিময় মূল্য দিয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে তাতে তাদের দুজনের কোন গুনাহ হবে না। (সূরা বাকারাঃ ২২৯)
হযরত সাবিত ইবনে কায়েমের স্ত্রী রাসূলে করীম (সা)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে বললেনঃ হে রাসূল! আমি আমার স্বামী সাবিত ইবনে কায়েমের চরিত্র ও দ্বীনদারীর দিক দিয়ে কোন দোষারোপ বা অভিযোগ করছি না। কিন্তু আসলে আমি তাকে পছন্দ করি না। নবী করীম (সা) জিজ্ঞেস করলেনঃ সে তোমাকে কি দিয়েছেল? তিনি বললেনঃ একটি বাগান। সে তালাকের বিনিময়ে সেই বাগানটি ফিরিয়ে দিতে রাজি কিনা জিজ্ঞেস কররে, সে বলল, জি হ্যাঁ। তখন নবী করীম (সা) সাবিতকে বললেনঃ ( আরবি******************)
তুমি বাগানটি ফিরিয়ে নাও এবং ওকে তালাক দিয়ে দাও।
এ পর্যয়ে মনে রাখা আবশ্যক যে, স্বামীর পক্ষ থেকে বাস্তবিকই কোন কারণ না থাকলে স্ত্রীর তালাক গ্রহণের জন্যে তাড়াহুড়া করা উচিত নয়। নবী করীম (সা) বলেছেনঃ ( আরবি******************)
যে মেয়েলোক কোন কারণ ব্যতিরেকেই স্বামীর কাছে তালাক চাইবে তার জন্যে জান্নাতের সুগন্ধিও হারাম হয়ে যাবে।
স্ত্রীকে জ্বালাতন করা হারাম
স্ত্রীকে এ উদ্দেশ্যে কষ্ট দেয়া যে, সে তাকে যা কিছু দিয়েছে তা ফিরিয়ে দিয়ে দিক এবং সে জন্যে তাকে জ্বালা-যন্ত্রণা দেয়া স্বামীর জন্যে সম্পূর্ণ হারাম। তবে সে যদি কোন প্রকাশ্য নির্লজ্জতার কাজ করে বসে তবে তা স্ব’তন্ত্র কথা। এ সম্পর্কেই আল্লাহ্ তা’আলা ইরশাদ করেছেনঃ ( আরবি******************)
তোমরা যা কিছু তোমাদের স্ত্রীদের দিয়েছ তার কোন অংশ ফিরিয়ে পাওয়ার উদ্দেশ্যে তোমরা তাদের কষ্ট দিও না। তবে তারা যদি কোন প্রকাশ্য নির্লজ্জতার কাজ করে, তবে তা স্বতন্ত্র কথা। (সূরা আন-নিসাঃ ১৯)
আর স্ত্রী যদি স্বামীর অপছন্দই হয় এবং সে নিজেই তাকে তালাক দিয়ে অপর কাউকে বিয়ে করতে ইচ্ছুক হয়ে থাকে, তাহলে স্ত্রীর কাছ থেকে কিছুই ফেরত লওয়া জায়েয নয়। আল্লাহ্ তা’আলা বলেছেনঃ ( আরবি******************)
তোমরাই যদি এক স্ত্রীর স্থলে আর এক স্ত্রী গ্রহণ করার ইচ্ছা করে থাক, আর তোমরা একজনকে বিপুল পরিমাণ মালমাত্তা দিয়ে থাক, তাহলে তোমরা তা থেকে কিছুই গ্রহণ করতে পারবে না। তোমরা কি দোষারোপ করে ও সুস্পষ্টভাবে অধিকার হরণ করে তা গ্রহণ করতে চাও? আর তা তোমাদের গ্রহণ করবেই বা কি করে? অথচ তোমরা পরস্পরের কাছ থেকে দাবি আদায় করে নিয়েছ। আর তারা তোমাদের কাছ থেকে শক্ত ও কঠিন প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছে।
স্ত্রী পরিত্যাগের ‘কসম খাওয়া’ হারাম
ইসলাম নরীর অধিকার আদায়ের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। তার একটা জ্বলন্ত প্রমাণ এই যে, স্বামী ক্রদ্ধ হয়ে স্ত্রীকে শয্যায় এত দীর্ঘ সময়ের জন্যে পরিত্যাগ করার কসম খাবে যা স্ত্রীর পক্ষে সহ্য করা বড়ই দুষ্কর, তা স্বামীর জন্যে ইসলাম সম্পূর্ণ হারাম ঘোষণা করেছে। স্বামী যদি স্ত্রী থেকে আলাদা থাকার কিরা-কসম খেয়ে বসে, তাহলে তাকে মাত্র চার মাসের অবকাশ দেয়া হয়েছে। এ সময়ের মধ্যে তার ক্রোধ ঠান্ডা হয়ে যাবে বলে আশা করা যায়। তখন সে তার ইচ্ছা পরিবর্তন করতে পারে। সে যদি এ চার মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বেই নিজ স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে নেয়, তাহলে ইতিমধ্যে তার এ কারণে যে গুনাহ হয়েছে, আল্লাহ্ তা মাফ করে দেবেন, তার জন্যে তার প্রশস্ত দরজা উন্মুক্ত করে দেবেন। তখন তার এ কিরা কসমের কাফফারা দেয়া ওয়াজিব। কিন্তু এ সময়কাল অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার মধ্যেও সে নিজ ইচ্ছা পরিবর্তন না করে ও ‘কসম’ না ভেঙ্গে, তাহলে তার স্ত্রী তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। স্ত্রীর অধিকার আদায়ে উপেক্ষা প্রদর্শনের এ-ই উচিত শাস্তি, সন্দেহ নেই।
কোন কোন ফিকাহবিদের মতে উপরিউক্ত সময়কাল অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তালাক সঙ্ঘটিত হবে। কাযী বা প্রশাসকের কোন ফয়সালার অপেক্ষায় থাকার কোন প্রয়োজন হবে না।
আবার অপর কোন কোন ফিকাহবিদ মনে করেন, মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়ার পর ব্যাপারটি প্রশাসকের সমীপে পেশ করা জরুরী। প্রশসক তাকে দুটো পস্থার যে কোন একটি গ্রহণের সুযোগ দেবে। হয় সে নিজের ইচ্ছায় পুনর্বিবেচনা করে স্ত্রীকে বাধ্য করে নেবে নতুবা সে তাকে তালাক দেবে। দুটোর মধ্যে যেটাই তার ভাল মনে হবে, সেটাই গ্রহণ করতে পারবে।
স্ত্রীর কাছে না যাওয়ার এ ‘কসম’কে শরীয়তের পরিভাষায় বলা হয় ‘ঈলা’। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা’আলা ইরশাদ করেছেনঃ ( আরবি******************)
যারা নিজেদের স্ত্রীদের সাথে সম্পর্ক না রাখার কসম খেয়ে বসে, তাদের জন্যে চার মাসের মেয়াদ দেয়া হলো। যদি তারা স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়, তাহলে আল্লাহ্ ক্ষমাশীল দয়াবান। আর যদি তালাক দেয়ারই সিদ্ধান্ত করে তাহলে আল্লাহ্ সব শোনেন, সব জানেন! (সূরা বাকারাহঃ ২২৬-২২৭)
চার মাসের সময় দেয়া হয়েছে এজন্যে যে, স্বামী যেন পুনর্বিবেচনা করার ও বুদ্ধি বিবেচনা সহকারে কাজ করার পূর্ণ সুযোগ লাভ করতে পারে। অপর দিকে একজন স্ত্রী স্বামীহীনা হয়ে খুব বেশের পক্ষে এ সময়কাল পর্যন্তই ধৈর্য ধারণ করে থাকতে পারে।
তাফসীরগণ এ পর্যায়ে হযরত উমরের একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন
এক রাতে তিনি যখন অবস্থা পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যে মদীনার অলিতে-গলিতে ঘুরতে লাগলেন, তখন তিনি একটি নারীর কণ্ঠস্বর শুনতে পান। তার স্বামী জিহাদের জন্যে দূরদেশে চলে গিয়েছিল। স্বামী-বিরহে কাতর হয়ে নারী করুন কন্ঠে গাইতেছিল।
রাত দীর্ঘ হয়ে গেছে চারদিকে অন্ধকার সমাচ্ছন্ন
আর আমাকে কাঁদাচ্ছে এ কথা যে,
আমার বন্ধু আমার কাছে নেই, যার সাথে আমি
খেলা করব।
আল্লাহর নামের শপথ, যদি আল্লাহর আযাবের
ভয় না থাকত,
তাহলে, এখনই এ পালঙ্কের বাহুগুলো
নড়ে উঠত।
হযরত উমর (রা) নারীর এই ফরিয়াদ শ্রবণ করে তাঁর কন্যা হযরত হাফসা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেনঃ স্বামী বিরহে নারী কতদিন ধৈর্যধারণ করে থাকতে পারে? তিনি বললেনঃ চার মাস। তখন আমীরুল মুমিনীন নির্দেশ দিয়ে দিলেনঃ কোন ব্যক্তিকে যেন তার নিজের স্ত্রী থেকে চার মাসের অধিককাল বিচ্ছিন্ন করে রাখা না হয়।
পিতামাতা ও সন্তানদের সম্পর্ক
বংশ সংরক্ষণ
সন্তান পিতার গোপনতত্ত্ব। তার বৈশিষ্ট্যাবলীর ধারক বাহক। জীবনে তার চোখের শীতলতা, তার মৃত্যুর পর তার অস্তিত্বের ধারা রক্ষাকারী। তার স্মৃতির প্রতীক। তার ভাল-মন্দ ও বৈশিষ্টসম্পন্ন গুণাবলীর উত্তরাধিকারী, তার কলিজার টুকরা, অন্তরের গভীর গহনে অবস্থানকারী সুষমা।
এ কারণেই আল্লাহ্ জ্বেনা-ব্যভিচার হারাম করেছেন। বিয়ে ফরয করে দিয়েছেন। যেন বংশ রক্ষা পায় এবং বিভিন্ন লোকের শুক্র সংমিশ্রিত হতে না পারে। সন্তান যেন পিতাকে চিনতে পারে, পিতাও চিনতে পারে তার সন্তানদের। বিয়ের মাধ্যমেই নারী বিশেষ কোন পুরুষের জন্যে নির্দিষ্ট ও সুরক্ষিত হয়ে যায়। স্বামীর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা তার জন্যে হারাম হয়ে দাঁড়ায়। বিয়ে হওয়ার পর স্বামী-স্ত্রীর ঘরে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করে, তা তার স্বামীর ঔরসজাত রূপে পরিচিত হয়। এ সম্পর্ক স্থাপনের জন্যে স্বতন্ত্র ভাবে কোন প্রমাণের প্রয়োজন হয় না। পিতারও ঘোষণার দরকার হয় না, মা’কে দাবি করতে হয় না এই বলে যে, আমার সন্তানের পিতা অমুক। কেননা নবী করীম (সা) বলেছেনঃ ( আরবি******************)
সন্তান তার, যার বিছানো শয্যায় তার জন্ম হয়েছে।
নিজ সন্তানের পিতৃত্ব অস্বীকার করা জায়েয নয়
এসব কারণে স্ত্রী স্বামীর শয্যায় তার সাথে সঠিকভাবে বিবাহিতা হয়ে যে সন্তান প্রসব করেছে, স্বামী তার পিতৃত্ব অস্বীকার করতে পারে না। তা করা তার জন্যে জায়েয নয়। এ অস্বীকৃতি তার স্ত্রী ও সন্তান উভয়ের জন্যেই খুবই লজ্জাকর ও মারাত্মত হয়ে থাকে। কাজেই নিছক ভিত্তিহীন কুধারণা, সন্দেহ কিংবা জনশ্রুতির অনস্বীকার্য লক্ষণাদির ভিত্তিতে স্বামীর দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে যে, স্ত্রী তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, তাহলে ইসলামী শরীয়ত সন্তান লালন-পালনের দায়িত্ব এমন ব্যক্তির কাঁধে চাপাতে চায় না, যে তাকে তার নিজের ঔরসজাত সন্তান বলে মানে না, জোরপূর্বক এ সন্তানকে তার উত্তরাধিকারী বানানও শরীয়তের নিয়ম নয়।
এক কথায় বলা যায়, ইসলামী শরীয়ত কোন স্বামীকে জীবনভর শোবা-সন্দেহের মধ্যে ফেলে রাখার পক্ষপাতী নয়। এ জটিলতা থেকে মুক্তি লাভের যে পন্থা ইসলাম উপস্থাপিত করেছে, পরিভাষায় তার নাম ‘লিয়ান’ ( আরবি******************)। অতএব যার নিজ স্ত্রী সম্পর্কে এ দৃঢ় প্রত্যয় কিংবা প্রবল ধারণা হবে যে, সে তার শয্যাকে ভিন্ পুরুষের শুক্র গ্রহণ করে কলঙ্কিত কেরেছে এবং তার গর্ভে অপর কোন পুরুষের ঔরসজাত সন্তান ধারণ করেছে, কিন্তু এ ব্যাপারের সত্যতায় কোন সাক্ষ্য পেশ করা তার কর্তব্য। বিচারক তাদের মধ্যে ‘লিয়ান’ করিয়ে দেবে। সূরা নূর-এ একথা বলা হয়েছে এ ভাষায়ঃ ( আরবি******************)
যারা নিজেদের স্ত্রীদের ওপর মিথ্যা দোষারোপ করবে এবং তাদের কাছে নিজের ছাড়া আর সাক্ষী থাকবে না, এমন ব্যক্তি সাক্ষ্য হচ্ছে এই যে, চারবার আল্লাহর নামে ‘কসম’- এই সাক্ষ্য দেবে যে, সে তার অভিযোগে সত্যবাদী। আর পঞ্চমবার বলবে যে, সে যদি মিথুক হয় তাহলে তার ওপর যেন আল্লাহর অভিশাপ হয়, আর সে স্ত্রীলোকটির শাস্তি এড়ান যায় এভাবে যে, সে বার বার আল্লাহর নামে ‘কসম’ খেয়ে এই সাক্ষ্য দেবে যে, এ পুরুষটি মিথ্যাবাদী। আর পঞ্চমবার বলবে, তার ওপর অভিশাপ হোক যদি পুরুষটি তার উত্থাপিত অভিযোগে সত্যবাদী হয়।
অতঃপর তাদের দুজনের মধ্যে চিরদিনের তরে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেয়া হবে এবং সন্তানকে মা’র সঙ্গে জুড়ে দেয়া হবে।
পালক পুত্র গ্রহণ হারাম
পিতার যেমন তার ঔরসজাত সন্তানের পিতৃত্ব অস্বীকার করার অধিকার নেই। অনুরূপভাবে যে সন্তান তার নিজ ঔরসজাত নয়, তাঁকে নিজের পুত্র বানান ও নিজের পুত্র বলে পরিচয় দেয়া ও দাবি করারও অধিকার নেই। জাহিলিয়াতের যুগে আরবরা অপরাপর জাতির লোকদের ন্যায় পালক পুত্র রেখে যার সাথে ইচ্ছা নিজের বংশ সম্পর্ক স্থাপন করত। যাকে ইচ্ছা নিজের পুত্র বানিয়ে নিত। এ পালিত পুত্রের কর্তব্য অধিকার ঠিক আপন ঔরসজাত পুত্রদের মতই হতো। পালিত পুত্রের পিতা ও বংশধারা জানা অবস্থায়ও এরূপ পালিত পুত্র বানানো হতো।
ইসলামের আগমনকালেও এরূপ পালক পুত্র বানানর রেওয়াজ ছিল তদানীন্তন আরব সমাজে। নবী করীম (সা) যায়দ ইবনে হারিসাকে এ জাহিলিয়াতের যুগে নবুওয়্যত প্রাপ্তির পূর্বে পুত্র বানিয়ে নিয়েছিলেন। কিন্তু ইসলাম ব্যাপারটিকে একটি অবস্তাব ও অসত্য ঘটনা রূপে দেখেছে। ইসলামের দৃষ্টিতে এক ভিন্ন ও অনাত্মীয় ব্যক্তিকে নিজ বংশের লোক বানিয়ে নেয়া ঘরের মেয়েদের সাথে ঠিক মুহররম পুরুষের মতো তাকে নিভৃত একাকীত্বে থাকতে দেয়া অথচ প্রকৃতপক্ষে সে এ মর্যাদার ব্যক্তি নয় এবং এ মেয়েরা তার জন্যে মুহররম নয়।
যে লোক কাউকে পালিত পুত্র বানায়, সে তাকে নিজের উত্তরাধিকারীও বানায়। এরূপ অবস্থায় আসল নিকটাত্মীয় উত্তরাধিকারীরা সম্পত্তির অংশ পাওয়ার অধিকারী হয়েও তারা তা থেকে বঞ্চিত থেকে যায়। তার দরুন প্রকৃত আত্মীয়দের মনে এই মুখে-ডাকা পুত্রের প্রতি একটা গোপন ক্ষোভ ও হিংসা-প্রতিহিংসা অতি স্বাভাবিকভাবেই জেগে উঠে। তার ফলে বিবাদ বিসম্বাদ ও সম্পর্কের অবনতি মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। কুরআন মজীদ এসব কারণেই এ জাহিলী ব্যবস্থাকে বাতিল ও সম্পূর্ণ অকাট্য হারাম ঘোষণা করেছে। আল্লাহ্ তা’আলা ইরশাদ করেছেনঃ ( আরবি******************)
তোমাদের মুখে-ডাকা পুত্রদেরকে তিনে (আল্লাহ্) তোমাদের প্রকৃত পুত্র বানিয়ে দেন নি। এ তো তোমাদের মুখ নিঃসৃত কথা মাত্র। কিন্তু আল্লাহই তো সত্য কথা বলেন, সঠিক ও নির্ভুল পথের সন্ধান দেন। ওদের ডাক ওদের পিতাদের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করে। আল্লাহর কাছে এটাই অধিকতর ইনসাফপূর্ণ কথা। কিন্তু ওদের পিতা যদি তোমাদের জানা না থাকে তাহলে ওরা তোমাদের দ্বীনি ভাই মাত্র। তোমাদের সাহায্যকারী বন্ধু মাত্র।
কুরআনের কথাঃ ‘এ তো তোমাদের মুখ-নিঃসৃত কথা স্পষ্ট করে বলে দিচ্ছে যে, মুখ-ডাকা পুত্র বা ধর্ম-পুত্র একেবারে অন্তঃসারশূন্য কথা, এরা পাশ্চাতে সত্য ভিত্তি বলতে কিছু নেই।
বস্তুত মুখ-নিঃসৃত কথা না প্রকৃত সত্যকে বদলে দিতে পারে, না পারে বাস্তবতাকে বদলে দিতে। অনাত্মীয় ব্যক্তি এর দ্বারাই আত্মীয় হয়ে যেতে পারে না। মুখে-ডাকা পুত্র কখনও হতে পারে না প্রকৃত নিজ ঔরসজাত সন্তান। মুখ-নিঃসৃত কথা পালিত পুত্রের দেহে রগে শিরায় কোলদার লালন-পালনকারী ব্যক্তির রক্ত প্রবাহিত করে দিতে পারে না, পারে না লালন – পালনকারী ব্যক্তির অন্তরে প্রকৃত পিতার পুত্র-বাৎসল্য ও স্নেহ-মমতা সৃষ্টি করতে। অনুরূপভাবে পালিত পুত্রের অন্তরে পিতৃভক্তির ভাবধারাও সৃষ্টি করতে পারে না। তার মধ্যে এ পরিবারের দৈহিক বিবেক-বুদ্ধীগত ও মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য-বিশেষত্বও সৃষ্টি করতে সম্পূর্ণ অসমর্থ।
এ পালক পুত্র গ্রহণ ব্যবস্থার সব রূপরেখা- উত্তরাধিকার আইন, পালিত পুত্রের (তালাক প্রদত্ত) স্ত্রীকে বিয়ে করা হারাম হওয়া ইত্যাদিও সম্পূর্ণরূপে বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে। কুরআন মজীদে যে উত্তরাধিকার আইন উপস্থাপন করা হয়েছে, তাতে রক্তের-স্ত্রীত্বের প্রকৃত নিকটাত্মীয়তার নয় এমন সম্পর্কের ওপর কোন গুরুত্ব দেয়া হয়নি। মীরাসে তাকে কোন অংশও দেয়া হয়নি।
( আরবি******************) রক্ত-সম্পর্কের আত্মীয়রা আল্লাহর আইনে পরস্পরের কাছে অধিক অধিকার সম্পন্ন।
বিয়ে সম্পর্কে কুরআন ঘোঘণা করেছে যে, নিজ ঔরসজাত পুত্রদের স্ত্রীরাই হারাম-মুহাররম, মুখে ডাকা পুত্রদের স্ত্রীরা নয়।
( আরবি******************) তোমাদের ঔরসজাত পুত্রদের স্ত্রীরাই তোমাদের জন্যে হারাম।
কাজেই পালিত পুত্রের স্ত্রী বিয়ে করা হারাম নয়, বরং সম্পূর্ণ জায়েয। কেননা প্রকৃতপক্ষে সে এক অনাত্মীয় ব্যক্তির স্ত্রী। অতএব সে যখন তার স্ত্রীকে তালাক দেবে (কিংবা সে মরে যাবে) তখন তাকে বিয়ে করতে কোন দোষ থাকতে পারে না।
পালক-পুত্র ব্যবস্থার বাস্তবভাবে রহিতকরণ
ব্যাপারটি কিছু মাত্র সহজ ছিল না। আরব সমাজের পালক পুত্র ব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত সুদৃঢ় ভিত্তিশীল। সমাজের গভীরে তার শিকড় নিবদ্ধ ছিল, লোকদের জীবনে তা গভীরভাবে সম্পর্কিত ছিল। এ কারণে আল্লাহ্ তা’আলা শুধু কথার নির্দেশ দ্বারাই এ ব্যরস্থার মূলোৎপাটন সম্ভব বলে মনে করেন নি, যথেষ্ট মনে করেন নি। তাই কথার সাথে সাথে বাস্তবভাবেও তা কার্যকর করার ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন।
আল্লাহর এ লক্ষ্য বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে স্বয়ং রাসূলে করীম (সা)-কেই কাজে লাগানর সিদ্ধান্ত নিলেন। যেন অতঃপর এ পর্যায়ে কোন শোবাহ সন্দেহ না থাকে, মুখে-ডাকা পুত্রের স্ত্রীকে বিয়ে করা জায়েয হওয়া সম্পর্কে আবহমান কাল থেকে চলে আসা দ্ধিধা-সংকোচ দূর করতে হলে এছাড়া আর কোন উপায়ও ছিল না, যথার্থ বা যথেষ্টও হতো না। আল্লাহ্ যা হালাল করেছেন চূড়ান্তভাবে তাকে হালাল মনে করা এবং আল্লাহ্ যা হারাম করেছেন, তাকেই চূড়ান্ত ভাবে হারাম মনে করার মতো দৃঢ় ঈমান ও বিশ্বাস সৃষ্টির জন্যে এটা ছিল একটা অপরিহার্য পদক্ষেপ।
হযরত যায়দা ইবনে হারিসা রাসূলে করীমের পালিত পুত্র ছিলেন। এ জন্যে তিনি সমাজে যায়দ ইবনে মুহাম্মাদ (সা) নামে সুপরিচিতি ছিলেন। তিনি যয়নব বিনতে জাহান নাম্মী এক মহিলাকে বিয়ে করেছিলেন। তিনি ছিলেন নবী করীম (সা)-এর ফুফাতো বোন। যয়নবের সাথে হযরত যায়দের দাম্পত্য সম্পর্কের অবনতি ঘটে। হযরত যায়দ এ বিষয়ে নবী করীম (সা)-এর কাছে বহু অভিযোগ করলেন। নবী করীম (সা) তাঁকে নানাভাবে বোঝাতে ও শিক্ষা দিতে লাগলেন। যদিও তিনি আল্লাহর জানিয়ে দেয়া সূত্রে জানতেন যে, যায়দ তাঁকে তালাক দেবেন এবং পরে তিনি নিজেই তাঁকে বিয়ে করবেন। কিন্তু মানবীয় দুর্বলতা কোন কোন মুহূর্তে দেখা দিত বলে তিনি মানুষের কুটক্তি ও দোষযুক্ত সমালোচনার ভয় করতেন। এজন্যে তিনি প্রতিবারে যখনই হযরত যায়দ অভিযোগ করতেন, তাঁকে বলতেনঃ ( আরবি******************)
হে যায়দ, তুমি তোমার স্ত্রীকে নিজের কাছেই রাখ এবং আল্লাহকে ভয় কর।
এ সময় কুরআনের যে আয়াত নাযিল হয়, তাতে রাসূলে করীম (সা)-কে ভর্ৎসনা করা হয়, বরং দীর্ঘকাল ধরে পালিত পুত্রের পরিত্যক্তা স্ত্রীকে বিয়ে করার ব্যাপারে সমাজে প্রচলিত ভুল ধারণা ও কুসংস্কার দূর করার জন্যে সমাজের মুকাবিলা করতে তাঁকে উদ্বুদ্ধ করা হয়। তাতে বলা হয়ঃ ( আরবি******************)
আল্লাহ্ যাকে নিয়ামত দিয়েছেন (ঈমান আনার সুযোগ দিয়ে), এবং তুমি যাকে নিয়ামত দিয়েছ (দাসত্ব শৃঙ্খল থেকে মুক্তি দিয়ে), সেই যায়দকে যখন তুমি বলতে, তুমি তোমার স্ত্রীকে তোমার নিজের জন্যে রাখ এবং আল্লাহকে ভয় কর, তখন তুমি তোমার মনে সেই কথা লুকিয়ে রাখতে যা আল্লাহ্ প্রকাশ করে দেবেন। আর তুমি মানুষকে ভয় পেতে অথচ আল্লাহকেই ভয় করা উচিত সর্বাধিক। পরে যায়দ যখন তার (স্ত্রী) থেকে তার প্রয়োজন পূর্ণ করে নিল, তখন তাকে সেই (যয়নব-যায়দের স্ত্রীকেই) তোমার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিলাম, যেন মুমিনদের মনে মুখে-ডাকা পুত্রদের স্ত্রীদের যখন তারা তাদের থেকে নিজেদের প্রয়োজন পূরণ করে দিয়ে ছেড়ে দেবে- বিয়ে করার ব্যাপারে কোনরূপ সংকোচ বা প্রতিবন্ধকতা অবশিষ্ট না থাকে। আর আল্লাহর ফরমান তো কার্যকর হবেই। (সূরা আহযাবঃ ৩৭)
পরবর্তী আয়াতে রাসূলের একাজে যে দোষারোপ করা হয়েছে তার প্রতিরোধ করা হয়েছে এবং বলিষ্ঠভাবে বলা হয়েছে যে, একাজ সম্পূর্ণ জায়েয, এতে কোন দোষ আদপেই নেই। বলা হয়েছেঃ ( আরবি******************)
আল্লাহ্ যা ফরয করে দিয়েছেন তার জন্যে তা করায় নবীর কোন দোষ ছিল না। এই আল্লাহর নিয়ম অতীত কাল থেকে। আর আল্লাহর ফয়সালা তো পরিমাণ মতোই। যারা আল্লাহর রিসালাত যথাযথভাবে পৌঁছিয়ে দেয় এবং তাঁকেই ভয় করে আল্লাহ্ ছাড়া আর কাউকেই ভয় করে না, হিসেব লওয়ার জন্যে আল্লাহই যথেষ্ট। মুহাম্মত তোমাদের পুরুষদের মধ্যের কারোরই পিতা নয়; বরং সে আল্লাহর রাসূল নবীগণের পরিসমাপ্তিকারী। আর আল্লহ্ তো সব বিষয়েই পূর্ণ মাত্রায় অবহিত।
শুধু লালন-পালনের উদ্দেশ্যে পুত্র বানানো এ পর্যন্ত যে পুত্র বানানো সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, ইসলাম তাকে বাতিল ও হারাম ঘোষণা কারেছে। তাতে এক ব্যক্তি জানে যে, পুত্র তার নয়, অপর কোন ব্যক্তির, তা সত্ত্বেও তাকে নিজের বংশ ও পরিবারের সাথে মিলিয়ে আপন করে নেয় এবং তার জন্যে আপন ঔরসজাত সন্তানের জন্যে প্রদত্ত যাবতীয় নিয়ম ও অধিকার প্রয়োগ করে। তাতে বংশের সংমিশ্রণ হয়, তার স্ত্রী বিয়ে করা হারাম হয়ে যায় এবং সে মীরাসের অংশ লাভ করে।
এছাড়া আরও এক প্রকার পুত্র বানানর রেওয়াজ রয়েছে। কিন্তু সে ধরনের পুত্র বানানকে ইসলাম হারাম করেনি। তা এ ভাবে হয় যে, কেউ কোন পরে পাওয়া কিংবা কোন ইয়াতীম ছেলে নিজের ঘরে নিয়ে নিল এবং তার প্রতি নিজের পুত্রের মতই স্নেহ-বাৎসল্য, আদর-যত্ন ও শিক্ষা-প্রশিক্ষণ দিল, তাকে খাওয়াল, পরাল, লালন পালন করে বড় করে তুলল ঠিক নিজের সন্তানের মতোই। কিন্তু এত সব করার পরও তাকে ‘নিজের পুত্র’ বলে অবহিত করল না, আপন পুত্রের জন্যে যে যে নিয়ম ও অধিকার তাও আরোপ করল না। এ ধরনের সেবা ও কল্যাণমূলক কাজ ইসলামে খুবই প্রশংসনীয় ও পছন্দনীয়। এরূপ কাজ যে করবে, সে নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে অশেষ সওয়াব পাবে, সে জান্নাত লাভ করবে। এ পর্যায়ে রাসূলে করীম (সা) বলেছেনঃ ( আরবি******************)
আমি এবং ইয়াতীমের দায়িত্ব গ্রহণকারী- লালন-পালনকারী জান্নাতে এ ভাবে থাকব- এই বলে তিনি তার শাহাদাত অঙ্গুলী ও মধ্যম অঙ্গুলী দ্বারা ইঙ্গিত করে ও দুটির মধ্যে ফাঁক করে দেখালেন।
হারিয়ে যাওয়া ছেলে কেউ পেলে তাকে ইয়াতীম মনে করতে হবে। পার্থিব সম্পর্কেও এ শব্দটি ভারভাবেই প্রযোজ্য। ইসলাম তার প্রতি লক্ষ রাখার জন্যে খুব তাগিদ করেছে।
কারো যদি কোন সন্তানাদি না থাকে এবং এরূপ কোন ছেলেকে সে কোন আর্থিক উপকার করার ইচ্ছা করে, তাহলে সে তার জীবনে বেঁচে থাকা অবস্থায়ই তার ধন-মাল থেকে যা ইচ্ছা দান করতে পারে এবং মৃত্যুর পূর্বে মোট সম্পদ-সম্পত্তির একতৃতীয়াংশের মধ্যে কিছু দেয়ার অসিয়তও করে যেতে পারে।
কৃত্রিম উপায় গর্ভ সৃষ্টি
জ্বেনা-ব্যভিচার ও পালিত পুত্রকে পুত্র বানান হারাম করে দিয়ে ইসলাম বংশের মর্যাদা রক্ষা করেছে। খারাপ ভাবধারা থেকে বংশকে পবিত্র রেখেছে।
এ কারণে কৃত্রিম উপায়ে গর্ভ সঞ্চারকে ইসলাম হারাম ঘোষণা করেছে, যদি তা স্বামী ছাড়া অন্য কারো শুক্র দ্বারা করান হয়। এরূপ অবস্থায় তা এক ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ ও ঘৃণ্য কাজ, সন্দেহ নেই। শায়খ শালতুত এ ফতোয়া দিয়েছেন। আসলে তা নতুন ধরনের জ্বেনা ছাড়া আর কিছু নয়, কেননা উভয় কাজের প্রকৃত অবস্থা সম্পূর্ণ অভিন্ন। তার ফলও এক। আর তা হচ্ছে স্বামী নয় এমন পুরুষের শুক্রবীজ গর্ভধারে ধারণ করা। প্রাকৃতিক আইন ও শরীয়তের বিধান- উভয়ের দৃষ্টিতেই এ কাজ অত্যন্ত জঘন্য।
কৃত্রিম উপায়ে গর্ভ সৃষ্টির কাজটি বাহ্যিক দৃষ্টিতে হয়ত কোন আইন ভঙ্গকারী কাজ নয়। কিন্তু সেটা আইনের দুর্বলতা ও ত্রুটি। আসলে তা জ্বেনাই- যা ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে এমন অপরাধ, যার ওপর অপরাধীকে ‘হদ্দ’- কঠোর শাস্তি দেয়া বাঞ্ছনীয়।
গর্ভ সৃষ্টির এ অভিনব পদ্ধতি যে অত্যন্ত মারাত্মক ও জঘন্য অপরাধ, তাতে কোন সন্দেহ নেই। পরের পুত্রকে নিজের পুত্র বলা অপরাধের চাইতেও অনেক বেশি মাত্রার অপরাধ। কেননা এ উপায়ে যে সন্তান জন্ম গ্রহণ করবে, তার মধ্যে দু ধরনেরই জঘন্যতা থাকবে। একটা হচ্ছে, পরের পুত্রকে নিজের পুত্র বলার জঘন্যতা। অর্থাৎ বংশে বংশের বাইরের লোককে গণ্য করা। আর দ্বিতীয় হচ্ছে চরিত্রহীনতা- জ্বেনার রূপ ধারণ। এ কাজকে না ইসলামী শরীয়ত সমর্থন করতে পারে, না কোন আইন। মনুষ্যত্বের মর্যাদা হারিয়ে পশুত্বের পর্যায়ে পৌছে যায়। তার পক্ষে সামাজিক মর্যাদার চেতনা লাভ আদৌ সম্ভবপর নয়।
প্রকৃত পিতা ছাড়া অন্য কাউকে পিতা বলা
নিজের ঔরসজাত সন্তানের পিতৃত্বকে অস্বীকার করা ইসলামে যেমন হারাম, তেমনি হারাম নিজের জন্মদাতা পিতা ছাড়া অন্য কাউকে পিতা বলা- নিজেকে অন্য কারো সন্তান বলা। নবী করীম (সা) এ কাজকে নিকৃষ্টতম কার্যাবলীর মধ্যে গণ্য কারেছেন। এর ফলে সে স্রষ্টা ও সৃষ্টি সকলেরই অভিশাপে পড়ে যায়। হযরত আলী (রা) বর্ণনা করেছেন- নবী করীম (সা) বলেছেনঃ ( আরবি******************)
যে লোক নিজেকে প্রকৃত পিতা ছাড়া অপর কারো সন্তান বলে প্রচার করবে কিংবা নিজের মনিব ছাড়া অপর কারো গোলাম হওয়ার কথা বলে বেড়াবে, তার ওপর আল্লাহ্ ফেরেশতা ও সমগ্র মানুষের অভিশাপ। কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তার কাছ থেকে না তওবা কবুল করবেন, না কোন বিনিময়। (বুখারী, মুসলিম)
হযরত সা’দ ইবনে আবূ ওয়াক্কাস (রা) বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (সা) ইরশাদ করেছেনঃ ( আরবি******************)
যে লোক নিজের পিতা ছাড়া অন্য কারো পুত্র হওয়ার দাবি করবে একথা জেনে শুনে যে, সে তার পিতা নয়, তাহলে জান্নাত তার জন্যে হারাম হবে।
সন্তান হত্যা করো না
এভাবেই ইসলাম মানব বংশকে রক্ষা করে তাকে অব্যাহত ধারায় অগ্রসর করে নিতে চাইছে। এজন্যে প্রত্যেক সন্তান ও পিতামাতার পরস্পরের অধিকার আদায় করা ওয়াজিব করে দিয়েছে, সে অধিকার ততখানি, যতখানি সন্তান বা পিতা হওয়ার দিক দিয়ে উপযুক্ত ও বাঞ্ছনীয় এবং এ অধিকারসমূহ পুরামাত্রায় সংরক্ষণের জন্যে কতগুলো বিষয় উভয়ের ওপর হারাম করে দিয়েছে।
সন্তানের রয়েছে জীবনে বেঁচে থাকার অধিকার। তাই পিতামাতার কোন অধিকার নেই সন্তানের জীবন বিনষ্ট করার, তাকে হত্যা করে হোক কিংবা গোপনভাবে তার অস্তিত্ব সঞ্চারিত হওয়ার পথে বাধা সৃষ্টি করেই হোক। জাহিলিয়াতের যুগের পিতামাতারা তাই করত। করত কন্যা সন্তান ও পুত্র সন্তান উভয়কেই। এ জন্যে আল্লাহ্ তা’আলা নির্দেশ দিয়েছেনঃ ( আরবি******************)
তোমরা দারিদ্রের ভয়ে তোমাদের সন্তান হত্যা করো না। আমি তাদের রিযিক দিই, তোমাদেরও আমিই দিচ্ছি। তাদের হত্যা করা অত্যন্ত বড় গুনাহ্ ও মারাত্মক ভুল।
( আরবি******************) জীবন্ত প্রোথিত করা কন্যাকে যখন কিয়ামতের দিন জিজ্ঞেস করা হবে কোন্ অপরাধে তাকে মেরে ফেলা হয়েছিল? (সূরা তাকভীরঃ ৮-৯)
এ জঘন্য ও বীভৎস কাজের উদ্বোধক যা-ই হোক, তা অর্থনৈতিক হোক- দারিদ্র্য ও খাবারের অভাব পড়ার ভয়েই হোক- কিংবা যেমন সামাজিক লজ্জার ভয়। মেয়ে হলে তদানীন্তন আরবে লজ্জায় তাকে হত্যা করা হতো। ইসলাম এ বর্বর ও পাশবিক কাজকে সম্পূর্ণ হারাম করে দিয়েছে। কেননা এ কাজের ফলে একটি জীবনকে হত্যা করা হয়, রক্ত সম্পর্কের অধিকার বিনষ্ট হয়। দুর্বল মানব সত্তার ওপর অত্যাচার ও জুলুম অনুষ্ঠিত হয়। এ কারণে নবী করীম (সা)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলঃ ( আরবি******************) কোন্ গুনাহটি সবচেয়ে বড় ও ভয়াবহ?
উত্তরে তিনি বলেছিলেনঃ ( আরবি******************)
তুমি আল্লাহর সঙ্গে কাউকে তার প্রতিদ্বন্দ্বী বানাবে- অথচ সেই এক আল্লাহই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। তারপর কোন্ গুনাহ বড় জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেনঃ তুমি তোমার সন্তানকে হত্যা করবে এ ভয়ে যে, সে তোমার সাথে খাওয়ায় শরীক হবে।
নবী করীম (সা) পুরুষদের ন্যায় স্ত্রীলোকদের কাছ থেকেও এ কথার ওপর বায়াআত গ্রহণ করেছেন যে, এ এক ভয়াবহ অপরাধ এবং সম্পূর্ণ হারাম। অতএব তা পরিহার করতে হবে। কুরআন মজীদে উদ্ধৃত হয়েছেঃ ( আরবি******************)
এই যে, তারা আল্লাহর সাথে এক বিন্দু শিরক করবে না, তারা চুরি করবে না, তারা জ্বেনা-ব্যভিচার করবে না এবং তারা তাদের সন্তান হত্যা করবে না। (সূরা মুমতাহিনাঃ ১২)
পিতার প্রতি সন্তানের দ্বিতীয় অধিকার হচ্ছে, পিতা তার জন্যে সুন্দর একটা নাম নির্দিষ্ট করবে। অতএব পিতার কর্তব্য সন্তানের এমন নাম না রাখা যার দরুন সে বড় হয়ে কোনরূপ লজ্জা কষ্ট পেতে পারে। দ্বিতীয়ত আল্লাহ্ ছাড়া অপর কারো বান্দা বা গোলাম হওয়ার অর্থের নামকরণও হারাম, যেমন আবদুনবী-নবীর দাস, আবদুল মসীহ্- ঈসা মসীর গোলাম ইত্যাদি।
তৃতীয়ত সন্তানের অধিকার হচ্ছে সে পুরোমাত্রার আদর-যত্ন পাবে, ভাল লালন-পালন ও খোর-পোশ পাবে। অতএব এসব ব্যাপারে কোনরূপ ঔদাসীন্য বা উপেক্ষা কিছু মাত্র জায়েয নয়। নবী করীম (সা) এ পর্যায়ে বলেছেনঃ ( আরবি******************)
তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেককেই তার দায়িত্ব বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।
তিনি বলেছেনঃ ( আরবি******************)
যার ওপর যাকে খাওয়ান-পরানর দায়িত্ব, সে ব্যাপারে উপেক্ষা ও অবহেলা করাই তার গুনাহগার হওয়ার জন্যে যথেষ্ট। (আবূ দাঊদ, নিসায়ী, হাকেম)
( আরবি******************) আল্লাহ্ তা’আলা প্রত্যেক দায়িত্বশীলকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন- এ বিষয়ে যে, সে তার দায়িত্ব পালন করেছে, না তার প্রতি উপেক্ষা দেখিয়েছে, তা বিনষ্ট হতে দিয়েছে। এমনকি প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার পরিবারবর্গ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে।
সন্তানদের মধ্যে সমতা রক্ষা
দেয়া-থোয়ার ব্যাপারে সন্তানদের মধ্যে সুষম ও পক্ষপাতহীন নীতি অবলম্বন করা, সমানভাবে স্নেহ মমতা করা ও সমানভাবে সকলের কল্যাণ কামনা পিতার কর্তব্য।
স্নেহ-বাৎসল্য, আদর-যত্ন ও দান-দক্ষিণা বিনা কারণে কাউকে অপরের অপেক্ষা অগ্রাধিকার দান- কোনরূপ বেশি-কম বা পক্ষপাতিত্ব করা সম্পূর্ণ হারাম। কেননা তাতে বঞ্চিত বা পেছনে পড়ে থাকা সন্তানদের মন প্রতিহিংসা জেগে উঠে। তাদের মনে শত্রুতা ও প্রতিহিংসার আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠতে পারে। এক্ষেত্রে পিতা ও মাতার উভয়ের সমান দায়িত্ব। নবী করীম (সা) ইরশাদ করেছেনঃ ( আরবি******************)
তোমরা তোমাদের পুত্র সন্তানদের মধ্যে পূর্ণ ইনসাফ করবে, তোমাদের পুত্র সন্তানদের মধ্যে পূর্ণভাবে সাম্য রক্ষা করবে, তোমাদের পুত্র-সন্তানদের মধ্যে সুষম বন্টন করবে সবকিছু। (আহমদ, নিসায়ী, আবূ দাউদ)
এ হাদীসের পটভূমিতে ঘটনা রয়েছে। বশীর ইবনে সায়দুল আনসারীর স্ত্রী তার পুত্র নুমান ইবনে বশিরের জন্যে তাঁর কাছে বিশেষ ধন-মাল যেমন বাগান ও ক্রীতদাস দেবার জন্যে দাবি করে ও এই দানকে সুদৃঢ় করিয়ে দেবার ইচ্ছা করে। আর এজন্যে এই দানের ওপর রাসূলে করীম (সা)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে বলেলেনঃ ( আরবি******************)
হে রাসূল! অমুকের মেয়ে (অর্থাৎ তার স্ত্রী) আমার কাছে দাবি করছে যে, আমি তার (আমার) পুত্রকে আমার ক্রীতদাস দিয়ে দেব। নবী করীম (সা) জিজ্ঞেস করলেনঃ তার কি আরও ভাই-বোন আছে? বললেনঃ হ্যাঁ। তখন তিনি বললেনঃ তাহলে তাদের প্রত্যেককেই কি এই রকম করে দেবে? বললেনঃ না। তখন নবী করীম (সা) বললেনঃ তাহলে তা কিছুতেই ভাল হবে না। আর আমি তো সত্য ও সুবিচার ছাড়া অন্য কিছুতেই সাক্ষী হতে পারব না। (মুসলিম, আহমদ, আবূ দাঊদ)
অপর বর্ণনায় রাসূলের কথার শেষ অংশ এইঃ ( আরবি******************)
আমাকে তুমি অবিচার ও হুকুমের ওপর সাক্ষী বানিও না। তোমার পুত্রদের যে অধিকার তোমার ওপর রয়েছে, তার মধ্যে এও একটি যে, তুমি তাদের মধ্যে ইনসাফপূর্ণ বন্টন করবে। যেমন তোমার অধিকার রয়েছে তাদের ওপর এবং যে, তারা তোমার খেদমত করবে। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তোমরা সন্তানদের মধ্যে ইনসাফ ও সুবিচার করবে। (বুখারী, মুসলিম, আবূ দাঊদ)
ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেনঃ সন্তানদের মধ্যে ধন বন্টনে পার্থক্য করা যায় যদি তার বাস্তবিকই কোন কারণ থাকে। যেমন দুর্বিপাকে পড়ার দরুন ঠেকায় পড়ে গেছে ও অপরাপরের অপেক্ষা বেশি অসুবিধার মধ্যে পড়ে যায়।
[আল মুগনী গ্রন্থে বলা হয়েছে, কোন রোগ, প্রয়োজন, অন্ধত্ব কিংবা বেশি সংখ্যক সন্তান হওয়া বা তার জ্ঞান অর্জনে মশগুল থাকার দরুন তাকে কিছু পরিমাণ বা বিশেষ কোন জিনিস দেয়া হলে অথবা কোন ছেলে খারাপ হয়ে যাওয়ার কারণে তাকে কিছু না দিলে ইমাম আহমদের মতে তা জায়েয হবে। তিনি বলেন, কোন কোন সন্তানকে বিশেষভাবে ওয়াকফ করে দেয়া প্রয়োজনের দরুন জায়েয, তাতে কোন দোষ হবে না। তবে বিনা কারণে ও বিনা প্রয়োজনে কাউকে কিছু বেশি বা বিশেষভাবে দিলে তাতে মাকরূহ হবে। দানের ব্যাপারেও এই হুকুম।]
মীরাস বন্টনে আল্লাহর আইন পালন
মীরাস বন্টনের ক্ষেত্রেও অনুরূপ ইনসাফপূর্ণ নীতি অবলম্বন করতে হবে। কাজেই কোন সন্তানকে মীরাস থেকে বঞ্চিত রাখা পিতার জন্যে জায়েয নয়। কোন আত্মীয়ের উত্তরাধিকারী আত্মীয়কে কৌশল করে বঞ্চিত রাখতে চেষ্টা করাও সম্পূর্ণ হারাম কাজ। কেননা মীরাস আল্লাহর জারী করা বিধান ও ব্যবস্থা। তিনি জেনে শুনে তার সুবিচার নীতি ও বিজ্ঞতা অনুযায়ী নিজেই এ ব্যবস্থা রচনা করেছেন। তাতে প্রত্যেক পাওনাদারকেই তার পাওনা অনুযায়ী অংশ দান করেছেন এবং তিনি লোকদের সেই বিধানের ওপর অবিচল হয়ে থাকার ও তদনুযায়ী কাজ অমান্য ও লংঘন করবে, সে তো তার আল্লাহকে দোষী সাব্যস্ত করবে।
আল্লাহ্ তা’আলা কুরআন মজীদের তিনটি আয়াতে মীরাম সংক্রান্ত যাবতীয় কথা বলে দিয়েছেন। প্রথম আয়াতের শেষে বলেছেনঃ ( আরবি******************)
তোমরা জান না, তোমাদের পিতা ও তোমাদের পুত্রদের মধ্যে ফায়দা ও উপকারের দিক দিয়ে তোমাদের অধিকতর নিকটবর্তী কে? এটা স্বয়ং আল্লাহরই অংশ বন্টন ও হিসসা নির্ধারণ। আর আল্লাহই হচ্ছেন সর্বজ্ঞ ও সর্বাধিক বিজ্ঞানী।
দ্বিতীয় আয়াতটির শেষে বলেছেনঃ ( আরবি******************)
কারো ক্ষতি না করেই- এটা আল্লাহর তরফ থেকে অসীয়ত। আর আল্লাহ্ সব কিছু জানেন ও পরম ধৈর্যশীল। এসব আল্লাহর নির্দিষ্ট সীমা। আর যে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য অনুসরণ করবে, আল্লাহ্ তাঁকে জান্নাতে দাখিল করবেন, তার পাদদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারা সদ্য প্রবাহমান। তারা তথায় চিরকাল থাকবে। আর এটা বিরাট সাফল্য। আর যে লোক আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করবে ও তাঁর নির্ধারিত সীমাগুলো লংঘন করবে, তাকে এমন জাহান্নামে দাখিল করবেন, যেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আর তার জন্যে লজ্জাকর অপমানকর আযাব রয়েছে।
মীরাস সংক্রান্ত তৃতীয় আয়াতের শেষে আল্লাহ্ তা’আলা বলেছেনঃ ( আরবি******************)
আল্লাহ্ তোমাদের কল্যাণের জন্যে সব কিছু স্পষ্ট করে বলে দিচ্ছেন, যেন তোমরা গুমরাহ হয়ে না যাও। আর আল্লাহ্ তো সব বিষয়েই পূর্ণ অবহিত।
অতএব মীরাসের যে বিধান আল্লাহ্ তা’আলা দিয়েছেন, যে লোক তার বিরোধিতা করবে, সে আল্লাহর বিস্তারিতভাবে বলে দেয়া প্রকৃত সত্য থেকে বিভ্রান্ত হয়ে গেছে। আল্লাহর নির্ধারিত সীমাকেও সে লংঘন করেছে। কাজেই তাকে আল্লহর আযাবের অপেক্ষায় থাকতে হবে। আর তা হচ্ছেঃ ( আরবি******************)
জাহান্নাম, চিরদিনই তাতে থাকবে এবং তার জন্যে আরও অপমানকর আযাব রয়েছে।
পিতামাতার সাথে সম্পর্ক ছিন্নকরণ
সন্তানের ওপর পিতামাতার বহু অধিকার রয়েছে। তাদের আনুগত্য করা, তাদের সাথে ভালভাবে কথাবার্তা বলা, তাদের প্রতি সম্মান শ্রদ্ধা প্রদর্শন প্রভৃতি সন্তানদের কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। মানব প্রকৃতিই তা করার জন্য তাগিদ জানায়, সুশোভনভাবে এ সব কাজের জন্যে মানুষকে অনুপ্রাণিত করে। মা’র ক্ষেত্রে এই কর্তব্য অধিকতর তাগিদপূর্ণ। কেননা মা-ই তাকে গর্ভে স্থান দিয়েছে, ক্রমাগত দশ মাস কাল তাকে গর্ভে বহন করেছে, তাকে প্রসব করার মারাত্মক ও মর্মান্তিক যন্ত্রণা ভোগ করেছে, তাকে নিজের বুকের স্তন চুষিয়েছে, রক্ত পানি করা দুগ্ধ পান করিয়াছে এবং অশৈশব তার রক্ষণাবেক্ষণ ও লালন-পালন করেছে। এতে তার যে কষ্ট হয়েছে, তা কোন ভাষা দিয়ে বর্ণনা করা যায় না। আল্লাহ্ নিজেই বলেছেনঃ ( আরবি******************)
আমরা মানুষকে তাগিদ করেছি এজন্যে, যেন তারা তাদের পিতামাতার সাথে ভাল ব্যবহার করে। তার মা কষ্ট স্বীকার করে তাকে বহন করেছে, প্রসব যন্ত্রণা সহ্য করেছে। আর ত্রিশ মাস কাল পর্যন্ত তাকে বহন ও দুগ্ধ পান করিয়েছে।
এক ব্যক্তি এসে রাসূলে করীম (সা)-কে জিজ্ঞেস করলঃ ( আরবি******************)
আমার সর্বোত্তম সাহায্য ও সেবা-যত্ন পাওয়ার সকলের মধ্যে সবচাইতে বেশি অধিকার কার?
জবাবে তিনি বললেনঃ তোমার মা’র। তারপর কে, তারপরে কে এবং তারপরে কে বেশি অধিকারী জিজ্ঞেসা করা হলে রাসূলে করীম (সা) প্রত্যেকবারই বললেনঃ ( আরবি******************) তোমার মা, তোমার মা, তোমার মা। তার পরের অধিকারী হচ্ছে ( আরবি******************) তোমার পিতা। (বুখারী, মুসলিম)
এ পিতামাতার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা, তাদের কষ্ট দেয়া সবচাইতে বড় কাবীরা গুনাহ্ বলে নবী করীম (সা) ঘোষণা করেছেন। তাঁর ঘোষণায় এ পাপটি হচ্ছে শিরকের পর বড় গুনাহ। নবী করীম (সা) বলেছেনঃ ( আরবি******************)
সবচাইতে বড় কবীরা গুনাহ্ কোনটি, আমি কি তা তোমাদের জানাব না? এ প্রশ্ন নবী করীম (সা) তিনবার করলেন। সাহাবিগণ বললেনঃ হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনি অবশ্যই তা আমাদের বলবেন। তখন তিনি বললেনঃ তা হচ্ছে আল্লাহর সাথে শরীক করা এবং পিতামাতার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা।
রাসূলে করীম (সা) আরও বলেছেনঃ ( আরবি******************)
তিনজন লোক কখনই জান্নাতে যাবে না। তারা হচ্ছেঃ পিতামাতার সাথে সম্পর্কচ্ছেদকারী, খারাপ ব্যবহারকারী, যে পুরুষ নিজ স্ত্রী দ্বারা খারাপ কাজ করায় এবং পুরুষালি চাল-চলন গ্রহণকারী নারী।
তিনি অপর এক হাদীসে বলেছেনঃ ( আরবি******************)
গুনাহগুলোর মধ্যে আল্লাহ্ যতটা চান তার শাস্তি কিয়ামতের দিন পর্যন্ত বিলম্বিত করবেন। কিন্তু তিনি পিতামাতার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ, খারাপ ব্যবহার করার পাপকে মৃত্যুর পূর্বে এ জীবনেই তড়িৎ ব্যবস্থায় শাস্তিতে পরিণত করবেন।
বিশেষ করে পিতামাতা বার্ধক্যে পৌঁছলে তাদের কল্যাণ কামনার জন্যে অধিক তাগিদ করা হয়েছে। কেননা এ সময় তাদের শক্তি সামর্থ্য নিঃশেষ হয়ে যায়। তখন তাদের দৈনন্দিন ব্যাপারে অধিক লক্ষ্য দেয়ার প্রয়োজন দেখা দেয়, বেশি বেশি যত্ন নেয়া আবশ্যক হয়ে পড়ে। এ সময় খুব দরদ সহানুভূতি ও ভক্তি-শ্রদ্ধা সহকারে যত্ন নেয়ার প্রয়োজন তীব্র হয়ে উঠে। এ কথাই আল্লহ্ বলেছেন নিম্নোদ্ধৃত আয়াতেঃ ( আরবি******************)
তোমার আল্লাহ্ ফরমান জারী করেছেন যে, তোমারা কারোরই দাসত্ব করবে না, কেবল মাত্র তাঁকে ছাড়া। আর পিতামাতার সাথে ভাল ব্যবহার আচরণ গ্রহণ করবে। তোমার কাছে তাদের একজন বা দুজনই যদি বার্ধক্যে পৌঁছে যায়, তাহলে তখন তাদের মনে কষ্ট হয় এমন কথা বলবে, না তাদের ভর্ৎসনা তিরষ্কার করবে না বরং তাদের সাথে সম্মানজনক কথা বলবে। তাদের খেদমতে বিনয় ও দরদমাখা বাহু বিছিয়ে দেবে এবং বলবে, হে আল্লাহ্! তুমি এ দুজনের প্রতি রহমত কর, যেমন করে তারা আমাকে ছোট-অবস্থায় লালন-পালন করেছে।
এ আয়াতের সমর্থনে হাদীসে বলা হয়েছেঃ ( আরবি******************)
পিতামাতাকে ‘উহ’ বলার অপেক্ষাও ছোট কোন ব্যবহার পিতামাতার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ ও খারাপ ব্যবহার পর্যায়ের থাকতে পারে বলে যদি আল্লাহ্ তা’আলা জানতেন, তাপলে তাও তিনি হারাম করে দিতেন।
পিতামাতাকে গালাগাল দেয়ার কারণ ঘটানোও কবীরা গুণাহ
এর চাইতেও বড় কথা হচ্ছে, নবী করীম (সা) পিতামাতাকে গালি খাওয়ানর কারণ ঘটানকেও হারাম ঘোষণা করেছেন। বরং তা হচ্ছে কবীরা গুণাহ্।
তিনি বলেছেনঃ ( আরবি******************)
পিতামাতাকে অভিশাপ দেয়াও সবচাইতে বড় কবীরা গুণাহ্। কোন বুদ্ধিমান ঈমানদার মানুষ পিতামাতাকে অভিশাপ দিতে পারে- অথচ তাদের দরুণই তার জীবন ও অস্তিত্ব লাভ সম্ভবপর হয়েছে- তা লোকদের বোধগম্য হলো না। তারা বিস্ময় সহকারে প্রশ্ন করলঃ কেমন করে একজন লোক তার পিতামাতাকে অভিশাপ দিতে পারে? জবাবে রাসূলে করীম (সা) বললেনঃ একজন অপর কারো পিতাকে গাল দেয়, সেও এর পিতাকে গাল দেয়। একজন অপর কারো মা’কে গালমন্দ বলে, সে-ও এর মা’কে গাল-মন্দ বলে- এভাবেই অভিশাপ দেয়ার কাজ সম্পন্ন হয়ে থাকে।
তাহলে যে লোক নিজেই তার পিতামাতাকে তাদের সম্মুখে গালাগাল করে, তার সম্পর্কে কি বলা যায়?
পিতামাতার অনুমতি ছাড়া জিহাদে যাওয়া
পিতামাতার অনুমতি ছাড়া জিহাদে চলে যাওয়াও হারাম করে দেয়া হয়েছে। কেননা ইসলামের দৃষ্টিতে পিতামাতার সন্তুষ্ঠি অধিক গুরুত্বপূর্ণ- অধিক কাম্য। তার তুলনায় জিহাদ হচ্ছে কম সফর কাজ, যদিও তাতে অনেক বেশি সওয়াব নিহিত রয়েছে, যা সারা রাত নামায পড়ে ও সারা বছর রোযা থেকেও পাওয়া যায় না।
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর ইবনুল আ’স (রা) বলেছেনঃ এক ব্যক্তি রাসূলে করীম (সা)-এর কাছে এসে জিহাদে যাওয়ার অনুমতি চাইলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ তোমার পিতামাতা জীবিত আছেন? বললেন, হ্যাঁ। তখন নবী করীম (সা) বললেনঃ ( আরবি******************)
তাহলে তুমি তাদের খেদমতে প্রাণপত করে দাও। অপর এক বর্ণনায় বলা হয়েছে, এক ব্যক্তি রাসূলে করীম (সা)-এর কাছে এসে বললেনঃ ( আরবি******************)
আমি আপনার কাছে হিজরত ও জিহাদ করার বায়’আত করব, তা করে আমি আল্লাহর কাছ থেকে সওয়াব পেতে চাই।
নবী করীম (সা) জিজ্ঞেস করলেনঃ তোমার পিতামাতার মধ্যে কেউ বেঁচে আছেন? বললঃ হ্যাঁ দুজনই বেঁচে আছেন। নবী করীম (সা) জিজ্ঞেস করলেনাঃ তুমি কি সত্যই আল্লাহর কাছ থেকে সওয়াব লাভ করতে চাও। বললঃ হ্যাঁ, চাই, তখন নবী করীম (সা) বললেনঃ ( আরবি******************)
তাহলে তুমি তোমার পিতা-মাতার কাছে ফিরে যাও এবং তাদের সাথে উত্তম সাহচর্য গ্রহণ কর।
অপর এক হাদীসের ভাষা এরূপঃ ( আরবি******************)
এক ব্যক্তি রাসূলে করীম (সা)-এর কাছে এসে বললঃ আমি আপনার কাছে হিজরতের বায়’আত করার উদ্দেশ্যে এসেছি আর আমার পিতামাতাকে ক্রন্দনরত অবস্থায় ফেলে রেখে এসেছি। একথা শুনে নবী করীম (সা) বললেনঃ তুমি তোমার পিতামাতার কাছে ফিরে যাও এবং যেমন তুমি তাঁদের কাঁদিয়েছ, তেমনি তাদের মুখে হাসি ফোটাও।
হযরত আবূ সায়ীদ (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, একজন ইয়ামেনী লোক হিজরত করে নবী করীম (সা)-এর কাছে উপস্থিত হলেন। তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়ামেনে তোমার কেউ আছে? বললেনঃ আমার পিতামাতা রয়েছেন। নবী করীম (সা) জিজ্ঞেস করলেনঃ তাঁরা কি তোমাকে অনুমতি দিয়েছেন। বললেনঃ না। তখন নবী করীম (সা) আদেশ করলেনঃ ( আরবি******************)
তুমি তোমার পিতামাতার কাছে ফিরে যাও এবং তাদের অনুমতি চাও, যদি তারা অনুমতি দেয়, তাহলে জিহাদে যাও নতুবা তাদের খেদমতে আত্মনিয়োগ করে থাক।
মুশরিক পিতামাতার সাথে ব্যবহার
যেহেতু ইসলাম পিতামাতার ব্যাপারে খুব বেশি গুরুত্ব আরোপ করে এজন্যে তারা মুশরিক হলেও তাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা ও তাদের প্রতি খারাপ আচরণ অবলম্বন করাকেও ইসলাম হারাম ঘোষণা করেছে। এমন কি তারা যদি শিরক কাজে খুব বেশি বাড়াবাড়ি করে, শিরক কাজের প্রতি আহ্বান জানায়, তার প্রচারকও হয় এবং তাদের মুসলিম পুত্রকে সেই শিরক কাজে নিয়ে যেতে চায়, তবুও তাদের সাথে কোনরূপ খারাপ ব্যবহার করা বা সম্পর্ক ছিন্ন করা যাবে না। কুরআন মজীদে বলা হয়েছেঃ ( আরবি******************)
তুমি শোকর কর আমার এবং তোমার পিতামাতার। ফিরে আমার কাছেই যেতে হবে। তারা দুজন যদি তোমাকে আমার সাথে শিরক করতে তোমার ওপর জোর প্রয়োগ করে, যে বিষয়ে তোমার কিছুই জানা নেই, তাহলে তাদের আনুগত্য করবে না। তবে তাদের সাথে ইহজীবনে ভাল সাহচর্য ও আচরণ অবলম্বন করবে। আর যে আমার দিকে একান্ত আত্মনিবেদিত, তুমি তার পথই অনুসরন কর। পরে আমার কাছেই তোমাদের সকলকে ফিরে আসতে হবে। তখন আমি তোমাদের জানিয়ে দেব তোমারা কি সব কাজকর্ম করছেলে? (সূরা লোকমানঃ ১৪-১৫)
এ আয়াত স্পষ্ট ভাষায় বলে দিচ্ছে যে মুশরিক পিতামাতা শিরক করতে বললে ও সেজন্যে বল প্রয়োগ করলে তাদের আনুগত্য করা বা তাদের আদেশ পালন করা যাবে না। কেননা আল্লাহর নাফরমানী হয় অপর যারই আনুগত্য করলে, তা কখনই করা যেতে পারে না। আল্লাহর সাথে শিরক করার তুলনায় বড় গুনাহ্ কি হতে পারে? কিন্তু তা সত্ত্বেও মুশরিক পিতামাতার সাথে দুনিয়ার জীবনে ভাল ব্যবহার করার আদেশ দেয়া হয়েছে। তাদের ঈমানী অবস্থা কি সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করা যাবে না বরং কেবলমাত্র আল্লাহর হুকুম বরদার নেককার লোকদের পথই অনুসরণ করতে থাকতে হবে। কেননা আল্লাহই হচ্ছেন সবচাইতে বড় হুকুমদাতা, বড় বিচারক- সেদিন যেদিন পিতামাতা সন্তানের কোন কাজে আসবে না, কোন সন্তানও কোন উপকার করতে পারবে না তার পিতামাতার।
বস্তুত উদারতা, ক্ষমাশীলতা ও ন্যায়বিচারের এ এমন এক উচ্চ উন্নত দৃষ্টান্ত, যার কোন তুলনাই দুনিয়ার অপর কোন ধর্ম কোন মতাদর্শই পেশ করতে পারবে না।
চতুর্থ অধ্যায়
আকীদা-বিশ্বাস ও ধর্মীয় অন্ধ অনুসরণ
পারস্পরিক কাজকর্ম ও লেনদেন
খেলা-তামাসা ও স্ফূর্তির অনুষ্ঠান
সামাজিক-সামষ্টিক সম্পর্ক-সম্বন্ধ
অমুসলিমদের সাথে সম্পর্ক
আকীদা-বিশ্বাস ও ধর্মীয় অন্ধ অনুসরণ
সুস্থ সঠিক ও নির্ভুল আকীদা-বিশ্বাসই হচ্ছে সমাজ ব্যবস্থার ভিত্তি। আর তওহীদ-সর্বতোভাবে আল্লাহ্ এক-একক ও অদ্বিতীয়- বিশ্বাসই হচ্ছে এ আকীদার নির্যাস এবং পূর্ণ দ্বীন ইসলামের প্রাণশক্তি। নির্ভুল আকীদা ও খালেস তওহীদের সংরক্ষণকেই ইসলাম তার শরীয়ত গঠনে ও শিক্ষার ভিত্তি স্থাপনে চরম লক্ষ্য হিসেবে সম্মুখে রেখেছে। সেই সাথে মূর্তি পূজারীরা যে জাহিলী আকীদা-বিশ্বাস ব্যাপকভাবে প্রচার করে রেখেছিল, তার বিরোধীতা ও মূলোৎপাটনও তাকে করতে হয়েছে। কেননা মুসলিম সমাজ-সামষ্টিকে শিরকের মলিনতা-কদর্যতা ও গুমরাহীর অবশিষ্ট থেকে রক্ষা করার জন্যে এ কাজ একান্তই অপরিহার্য।
আল্লাহর সুন্নাতের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা
ইসলাম তার অনুসারীদের মন-মগজে সর্বপ্রথম এ বিশ্বলোক সংক্রান্ত দর্শনকে সুদৃঢ় করেছে। ইসলাম ঘোষণা করেছে, মানুষ এ বিশ্বলোকের বিরাট ব্যবস্থার অধীন তার পৃথিবীর ওপর ও আকাশ মণ্ডলের নিচে জীবন যাপন করে। এ বিরাট বিশ্বলোক কোন ‘মগের মুল্লুক’ নয়, ছেলে-শিশুদের খেলনা নয়। তা হেদায়েতের বিধান ছাড়া চলছে না, ইচ্ছামত যত্রতত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে না। তা কোন সৃষ্টির কামনা-বাসনা অনুযায়ীও চালিত হচ্ছে না। কেননা সৃষ্টির কামনা-বাসনা এক ও অভিন্ন নয়, পরস্পর সামঞ্জস্য সম্পন্ন নয় বরং পরস্পর সাংঘর্ষিক। তাও যে বিভ্রান্ত ও দিশেহারা তা-ও নিঃসন্দেহ। কুরআন মজীদে বলা হয়েছেঃ ( আরবি******************)
প্রকৃত মহাসত্য যদি তাদের কামনা বাসনা অনুসরণ করে চলত, তাহলে আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী এবং তার মধ্যে যা কিছু আছে, তা সবই ধ্বংস ও চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যেত। (সূরা আল-মুমিনীনঃ ৭১)
বস্তুত এ বিশ্বলোক প্রাকৃতিক আইন ও আল্লাহ্ প্রদত্ত সুন্নাতের সুদৃঢ় বন্ধনে বন্দী। এ নিয়ম ও আল্লাহ্ প্রদত্ত সুন্নাতের কোন পরিবর্তন নেই, তাতে নেই কোনরূপ ব্যতিক্রম। কুরআন মজীদের কয়েকটি স্থানেই এ কথা বলিষ্ঠ ঘোষিত হয়েছে। সূরা ফাতির-এ বলা হয়েছেঃ ( আরবি******************)
আল্লাহর সুন্নাত- নিয়ম-কানুনে কোনরূপ পরিবর্তন বা ব্যতিক্রম দেখতে পাবে না।
কুরআন ও সুন্নাত মুসলমানকে শিক্ষা দিয়েছে যে, এসব প্রাকৃতিক নিয়ম-কানুনকে সম্মান করা- তার মর্যাদা রক্ষা করা কর্তব্য। কার্যকারণ প্রয়োগে ফলাফল লাভের জন্যে চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালাবে। কেননা আল্লাহ্ প্রতিটি কাজের মূলে ‘কারণ’ রেখেছেন এবং এ দুয়ের মধ্যে গভীর সম্পর্ক সংস্থাপন করে নিয়েছেন। ইবাদতগাহের পরিচালক, ধোঁকা প্রতারণার পেশাধারী ও ধর্ম-ব্যবসায়ীরা নিজেদের সার্থোদ্ধারের মতলবে যে সব কাল্পনিক গোপন কার্যকারণকে উপার্জন উপায়রূপে অবলম্বন করেছে, তার প্রতি কোন মুসলমানই একবিন্দু ভ্রুক্ষেপ করতে ও তার গুরুত্ব মেনে নিতে পারে না।
কুসংস্কার ও ভিত্তিহীন বিশ্বাসের বিরুদ্ধে লড়াই
বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (সা) যখন দুনিয়ায় আগমন করলেন, তখন তিনি সমাজে ধোঁকাবাজদের দল-কে দল দেখতে পেলেন। তারা গণকদার বা জ্যোতিষী নামে পরিচিত ছিল। গায়েবের অতীত বা ভবিষ্যতে সঙ্ঘটিত বা ব্যাপারাদি জ্বিনদের মাধ্যমে জেনে নিতে পারে বলে দাবি করত। এ ধোঁকা-প্রতারণা কুরআন ও সুন্নাতের সম্পূর্ণ পরিপন্থী বলে নবী করীম (সা) তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। তিনি সকলকে আল্লাহর কালাম শোনালেনঃ ( আরবি******************)
আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীতে যারাই রয়েছে তারা কেউই ‘গায়ব’ জানে না, সব কিছু জানেন একমাত্র আল্লাহ্। (সূরা নামলঃ ৬৫)
অতএব ফেরেশতা, জ্বিন বা মানুষ কেউই ‘গায়ব’ জানতে পারে না।
রাসূলে করীম (সা) আল্লাহর এ ঘোষণাও পাঠ করে শোনালেনঃ ( আরবি******************)
আমি (মুহাম্মাদ) যদি গায়ব জানতাম, তাহলে বেশি বেশি কল্যাণ ও মঙ্গল আমি নিজের জন্যে করে নিতাম এবং কোনরূপ খারাবী আমাকে স্পর্শ পর্যন্তও করতে পারত না। আমি তো শুধু প্রদর্শনকারী, সুসংবাদদাতা ঈমানদার লোকদের জন্যে।
হযরত সুলায়মানের খেদমতে নিয়োজিত জ্বিনদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা’আলা জানিয়ে দিলেনঃ ( আরবি******************)
ওরা যদি গায়ব জানতই, তাহলে তারা সেই অপমানকর আযাবে দীর্ঘদিন বন্দী হয়ে থাকত না। (সূরা সাবাঃ ১৪)
অতএব যে লোক প্রকৃত গায়ব জানার দাবি করে, সে আল্লাহ্, প্রকৃত ব্যাপারে এবং সমস্ত মানুষের ওপর সম্পূর্ণ ও সুস্পষ্ট মিথ্যা আরোপ করে।
নবী করীম (সা)-এর কাছে বিভিন্ন প্রতিনিধি দল এসে উপস্থিত হয়েছিল। তাদের ধারণা ছিল, নবী করীম (সা)-ও বুঝি গায়ব জানার দাবি করেছেন। এ ব্যাপারে তারা নবী করীম (সা)-এর পরীক্ষাকরণের উদ্দেশ্যে হাতের মুঠির মধ্যে কিছু গোপন করে জিজ্ঞেস করলঃ ‘বলুন তো আমাদের মুঠোর মধ্যে কি আছ।’ নবী করীম (সা) তাদের স্পষ্ট ভাষায় বলে দিলেনঃ ( আরবি******************)
আমি কোন গণকদার নই। জেনে রাখ, গণকদার, গণকদারী ও গণকদার গোষ্ঠী সকলেই জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।
গণকদারকে বিশ্বাস করা কুফর
ইসলাম কেবল গণকদার ও ধোঁকাবাজ প্রতারকদের বিরুদ্ধে কথা বলেই ক্ষান্ত হয়নি। যারা নিজেদের কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও ভ্রান্ত ধারণা সম্পন্ন হওয়ার দরুন তাদের কাছে যায়, জিজ্ঞস করে ও জানতে চায় এবং তাদের সত্য বলে বিশ্বাস করে, তাদেরকেও ইসলাম ওদের সঙ্গেই শরীক করে নিয়েছে এবং উভয় শ্রেণীর লোকদের অভিন্ন পরিণতির কথা ঘোষণা করেছে। নবী করীম (সা) বলেছেনঃ ( আরবি******************)
যে লোক জ্যোতিষীর কাছে গেল, তাকে কোন বিষয়ে জিজ্ঞেস করল এবং সে যা বলল তাতে তাকে সত্যবাদী বলে বিশ্বাস করে নিল, চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার কোন নামাযই কবুল হবে না।
অপর হাদীসে বলা হয়েছেঃ ( আরবি******************)
যে লোক গণকদারের কাছে গেল এবং সে যা বলল, ততে তাকে সত্য বলে বিশ্বাস করল, সে হযরত মুহাম্মদের প্রতি অবতীর্ণ দ্বীনকে অবিশ্বাস করল- কাফির হয়ে গেল। (বাজ্জার)
তা এজন্যে যে, মুহাম্মাদ (সা)-এর প্রতি নাযিল হয়েছে যে, গায়েব কেবলমাত্র আল্লাহই জানেন, মুহাম্মাদ (সা) গায়ব জানেন না, অন্যরা তো বটেই। কুরআন মজীদে বলা হয়েছেঃ ( আরবি******************)
বল, আমি বলছি না যে, আমার কাছে আল্লাহর ভাণ্ডারসমূহ রয়েছে, আমি গায়বও জানি না, আমি তোমাদের একথাও বলছি না যে, আমি একজন ফেরেশতা। আমি তো অনুসরণ করি শুধু তাই যা আমার কাছে ওহী হয়ে আসে।
মুসরমান যখন কুরআন মজীদ থেকে একথা স্পষ্ট ও অকাট্যভাবে জানতে পারল, তার পরও বিশ্বাস করল যে, কোন কোন সৃষ্টি- মানুষ বা জ্বিন্- তকদীরের নিগূঢ় রহস্য উদঘাটন করতে সক্ষম এবং তারা গয়বী জগতের জ্ঞানের অধিকারী, তাহলে তারা হযরত মুহাম্মাদ (সা)-এর কাছে অবতীর্ণ দ্বীন-ইসলামকে সম্পূর্ণরূপেই অস্বীকার করল, তার প্রতি অবিশ্বাস প্রকাশ করল।
পাশার দ্বারা ভাগ্য জানতে চাওয়া
পূর্বোল্লেখিত যুক্তির ভিত্তিতেই ইসলাম পাশার সাহায্যে ভাগ্য জানতে চাওয়াকে সম্পূর্ণ হারাম করে দিয়েছে।
‘পাশা’ বলতে এখানে বোঝানো হয়েছে, কতগুলো তীর। জাহিলিয়াতের যুগে আরবরা তার সাহায্যে ভাগ্য জানবার জন্যে চেষ্টা করত, সেজন্যে সেগুলোকে ব্যবহার করত। তার একটার উপর লেখা থাকত, ‘আমাকে আমার আল্লাহ্ নির্দেশ দিয়েছেন’। দ্বিতীয়টির ওপর লেখা থাকত, ‘আমাকে আমার আল্লাহ্ নিষেধ করেছেন’। তৃতীয়টি থাকত সম্পূর্ণ খালি। তার ওপরু কিছুই লেখা থাকত না। তারা যখন বিদেশ যাত্রার ইচ্ছা করত কিংবা বিয়ে ইত্যাদি কাজের ইচ্ছা করত, তখন তারা মূর্তির ঘরে উপস্থিত হতো। আর তাতেই রক্ষিত থাকত এই তীরসমূহ। এখন তাদের ভাগ্যে কি লেখা আছে তা তারা জানতে চাইত। যদি প্রথম তীরটি- যাতে ‘আদেশ করেছেন’ লেখা রয়েছে- বের হতো, তাহলে তারা অগ্রসর হতো। আর যদি নিষেধ লেখা তীরটি বের হতো, তাহলে তারা প্রস্তাবিত কাজ থেকে বিরত থাকত। আর খালি তীরটি বের হলে তারা বারবার তীর বের করত- যেন সুস্পষ্ট নির্দেশ পাওয়া যায়।
আমাদের সমাজে জাহিলিয়াতের ঠিক এ ধরনটি প্রচলিত না থাকলেও এর সাথে সাদৃশ্য সম্পন্ন বেশ কিছু কাজ প্রচলিত রয়েছে। যেমন ‘রমন’ কড়ি, কিতাব খুলে ফাল লওয়া। তাসের পাতা বা পেয়ালা পড়া ইত্যাদি এ পর্যায়ে যা কিছু করা হয়, ইসলামে তা সবই সম্পূর্ণ হারাম।
আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের প্রতি যেসব খাদ্য হারাম করেছেন, তার উল্লেখের পর বলেছেনঃ ( আরবি******************)
তোমরা তীরসমূহ দ্বারা ভাগ্য জানতে চাইবে, তা হারাম, তা আল্লাহর আইন লংঘনমূলক কাজ। (সূরা মায়িদাঃ ৩)
আর নবী করীম (সা) বলেছেনঃ ( আরবি******************)
যে লোক গণকদারী করল কিংবা তীর দ্বারা ভাগ্য জানতে চেষ্টা করল অথবা খারাপ ‘ফাল’ লওয়ার দরুন বিদেশ সফর থেকে ফিরে গেল, সে উচ্চতর মর্যাদা লাভ করতে পারবে না কখনও। (বুখারী, মুসলিম)
যাদুবিদ্যা
আনুরূপভাবে ইসলাম যাদুবিদ্যা ও যাদুকরদের মুকাবিলা করেছে। যারা যাদুবিদ্যা শিখে, তাদের সম্পর্কে কুরআন মজীদে বলা হয়েছেঃ ( আরবি******************)
তারা এমন বিদ্যা শিখে যা তাদের ক্ষতি করে, কোন উপকার দেয় না।
নবী করীম (সা) যাদু কার্যকে ধ্বংসকারী কবীরা গুনাহর মধ্যে গণ্য করেছেন. তা ব্যক্তির পূর্বে জাতিকে ধ্বংস করে। পরকালের পূর্বে এ দুনিয়াই যাদুকররা চরমভাবে বিপর্যয়ের মধ্যে ঠেলে নিয়ে যায়। নবী করীম (সা) বলেছেনঃ ( আরবি******************)
তোমরা সাতটি ধ্বংসকারী কাজ থেকে বিরত থাক। সাহাবিগণ বললেনঃ হে রাসূল, সে সাতটি কি কি? তিনি বললেনঃ আল্লাহর সাথে শিরক করা, যাদুবিদ্যা, আল্লাহ্ যে প্রাণী হত্যা করাকে হারাম করেছেন- ইনসাফের ভিত্তিতে হত্যা করা ছাড়া- সেই নর হত্যা, সুদ খাওয়া, ইয়াতীমের ধন-মাল ভক্ষণ-হরণ, যুদ্ধের ময়দান থেকে পৃষ্ঠ-প্রদর্শন এবং ঈমানদার অসতর্ক মহিলাদের সম্পর্কে মিথ্যা মিথ্যা ব্যভিচারের দোষারোপ করা। (বুখারী, মুসলিম)
কোন কোন ফিকাহবিদ যাদুবিদ্যা বা যাদুকার্যকে কুফরি বলেছেন, কিংবা বলেছেন, তা মানুষকে কুফরি পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। অপর কোন কোন ফিকাহবিদ এ মত দিয়েছেন যে, যাদুকরের দুষ্কৃতি থেকে সমাজকে পবিত্র রাখার জন্যে তাকে হত্যা করা ওয়াজিব।
কুরআন মজীদ আমাদের শিক্ষা দিয়েছে যাদুকরদের দুষ্কৃতি ও ক্ষতি থেকে আল্লাহর কাছে পানা চাওয়ারঃ ( আরবি******************)
ফুঁ দিয়ে গিয়ে কসে বাঁধে যেসব নারী, তাদের দুষ্কৃতি ও ক্ষতি থেকে, হে আল্লাহ্ তোমার কাছে পানা চাই।
গিড়ের মধ্যে ফুঁ দেয়া যাদু করার একটা পদ্ধতি এবং এটা যাদুকরদের একটা বিশেষ ধরনের কাজ। হাদীসে বলা হয়েছেঃ ( আরবি******************)
যে লোক গিড়েতে ফুঁ দিল, সে যাদু করল। আর যে যাদু করল সে শিরক করল।
গণদারদের কাছে যাওয়া এবং গায়বী ও রহস্যাবৃত বিষয়াদি জানতে চেষ্টা করাকে যেমন ইসলাম হারাম ঘোষণা করেছে, তেমনি যাদু বা যাদুকরদের কাছে কোন রোগের চিকিৎসার্থে বা কোন সমস্যার সমাধানের জন্যে আশ্রয় গ্রহণকেও সম্পূর্ণ হারাম করে দিয়েছে। নবী করীম (সা) এ কাজ থেকে সম্পূর্ণ নিঃসম্পর্কতার কথা ঘোষণা করেছেন। বলেছেনঃ ( আরবি******************)
যে লোক গণকদারী করল বা যার জন্যে গণকদারী করা হলো, যে ফাল গ্রহণ করল কিংবা যার জন্যে ফাল গ্রহণ করা হলো কিংবা যে যাদুগিরি করল বা যার জন্যে যাদুগিরি করা হলো, সে আমার উম্মতের মধ্যে গণ্য নয়।
হযরত ইবনে মাসঊদ বলেছেনঃ ( আরবি******************)
যে লোক কোন গণকদার বা যাদুকর কিংবা গায়বী কথা বলার লোকের কাছে গেল, তাকে জিজ্ঞেস করল এবং সে যা বলল তা সে সত্য বলে বিশ্বাস করল, সে মুহাম্মাদ (সা)-এর প্রতি অবতীর্ণ দ্বীন-ইসলামকে অস্বীকৃতি জানাল, তা অবিশ্বাস করল।
রাসূলে করীম (সা) আরও বলেছেনঃ ( আরবি******************)
মদ্যপায়ী, যাদু বিদ্যায় বিশ্বাসী ও রক্তসম্পর্ক ছিন্নকারী কখনই জান্নাতে যাবে না।
এসব হাদীসের আলোকে জানা গেল যে, কেবল যাদুকরের কাজই হারাম নয়, যাদুবিদ্যায় বিশ্বাসী এবং গণকদার বলে তাকে যে সত্য মানে, তার এ কাজও সম্পূর্ণ হারাম।
যদি মূলত হারাম কাজের উদ্দেশ্যে এ যাদুবিদ্যা ব্যবহৃত হয়, যেমন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টি, দৈহিক ক্ষতি সাধন প্রভৃতি তাহলে আরও কঠিন হারাম হয়ে দাড়ায়, আর যাদুকররা যে সাধারণত এসব কাজ করে তা সকলেই জানেন।
তাবীজ ব্যবহার
তাবীজ-তুমার ব্যবহারও এ পর্যায়েরই কাজ। তাতে এ বিশ্বাস মনে নিহিত থাকে যে, তাবীজ বাঁধলেই রোগ সেরে যাবে বা রোগের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে। এই বিংশ শতাব্দীর আলোকোজ্জ্বল যুগেও এমন বহু লোকই রয়েছে যারা নিজেদের ঘরের দুয়ারে ঘোড়ার ‘জুতা’ বাঁধে। আজকের দুনিয়ায় এমন লোকেরও অভাব নেই যারা জনগণের মূর্খতা-অজ্ঞতার সুযোগে বৈষয়িক অর্থনৈতিক স্বার্থ উদ্ধার করার কাজে দিন-রাত ব্যস্ত। তারা তাদের জন্যে তাবীজ লিখে। এসব তাবীজে রেখা ও ধাঁধা অঙ্কিত থাকে। তারা তাদের সম্মুখে কিরা-কসম করে নিজেদের সত্যতা ও দৃঢ় সংকল্প প্রকাশ করে। মন্ত্র পড়ে তাবীজের ওপর ফুঁ দেয়। দাবি করে যে, তাবীজ-তুমার বাঁধলে জ্বিনের কুপ্রভাব পড়তে পারে না, ভূত-প্রেত, কুদৃষ্টি বা হিংসা-পরশ্রীকাতরতা প্রভৃতি কোন ক্ষতি করতে পারবে না। কিন্তু এসব ইসলাম সমর্থিত চিকিৎসা পদ্ধতি নয়।
রোগমুক্তি, রোগ প্রতিরোধ ও রোগের আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্যে ইসলাম পরিচিত পদ্ধতি বিধিবদ্ধ করেছে। যারা সে সব পরিহার-প্রত্যাখ্যান করে গুমরাহীর পথ অবলম্বন করে তাদের তিরষ্কার করেছে।
নবী করীম (সা) বলেছেনঃ ( আরবি******************)
তোমরা রোগের চিকিৎসার্থে ঔষধ ব্যবহার কর। কেননা যিনি রোগ সৃষ্টি করেছেন, তিনি তার ঔষধও সৃষ্টি করেছেন। (বুখারী)
তিনি আরও বলেছেনঃ ( আরবি******************)
তোমাদের এ সব ঔষধের মধ্যে তিনটি জিনিস খুবই উপকারী। তা হচ্ছে, মধু পান করা, রক্ত চুসার ছুরি কিংবা আগুনে দাগাঁনো। (বুখারী, মুসলিম)
একটু চিন্তা করলেই দেখা যাবে, রাসূলে করীমের বিশেষ উপকারী এ তিনটি ঔষধই চিকিৎসা প্রক্রিয়ার আধুনিক কালের চিকিৎসা ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হয়ে রয়েছে। মুখে খাওয়া ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা, অস্ত্রোপাচারের সাহায্যে রোগমুক্তি এবং দাগানো পন্থায় রোগের নিরাময়তা অর্জন। বিদ্যুৎ তাপ বা ছ্যাঁকের চিকিৎসা এই তৃতীয় পর্যায়ের মধ্যে শামিল এবং তা অত্যাধুনিক পদ্ধতি। অতএব এ সব চিকিৎসাই বৈধ।
রোগ প্রতিরোধ বা চিকিৎসার উদ্দেশ্যে তাবীজ বাঁধা কিংবা যাদু-মন্ত্র পাঠ সুস্পষ্ট মুর্খতা ও গুমরাহী এবং তা আল্লাহ্ প্রদত্ত সুন্নাত ও তওহীদী আকীদার পারিপন্থী। হযরত ওকবা ইবনে আমের (রা) বলেনঃ দশ ব্যক্তি সমন্বয়ে সঠিক এক প্রতিনিধিদল নবী করীমের খেদমতে উপস্থিত হলো, তন্মধ্যে নয়জনের কাছ থেকে তিনি বায়’আত গ্রহণ করলেন, একজনের বায়’আত নিলেন না। তাদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বললেনঃ ( আরবি******************)
ও লোকটির বাহুতে তাবীজ বাঁধা রয়েছে। এ কথা শুনে লোকটি তাবীজ ছিঁড়ে ফেলল। পরে নবী করীম (সা) তারও বায়’আত গ্রহণ করলেন, এবং পরে বললেনঃ যে লোক তাবীজ বাঁধে সে শিরক করে। (আহমদ, হাকেম)
অপর হাদীসে বলা হয়েছেঃ ( আরবি******************)
যে লোক তাবীজ বেঁধেছে, আল্লাহ্ তাকে সাফল্যমণ্ডিত করবেন না। আর যে লোক মাদুলী বাধল, আল্লাহ্ তাকে একবিন্দু শন্তি ও স্বস্তি দেবেন না। (আহমদ)
ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) বলেন, নবী করীম (সা) এব ব্যক্তির বাহুতে পিতলের মাদুলি বা কবজ বাঁধা দেখতে পেলেন। বললেনঃ তোমার জন্যে আফসোস! তুমি ওটা কি বেঁধে রেখেছ? বললঃ এটা দুর্বলতা দূর করার উদ্দেশ্যে বেঁধেছি। তখন নবী করীম (সা) বললেনঃ ( আরবি******************)
ওটা তোমার দুর্বলতা অধিক বৃদ্ধি করবে, ওটা ফেলে দাও। নতুবা ওটা বাধা অবস্থায় যদি তোমার মৃত্যু হয়, তাহলে কস্মিনকালেও তুমি কল্যাণ পেতে পারবে না। (আহমদ, ইবনে হাব্বান)
এ সব শিক্ষা সাহাবিগণের ওপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিল বলে তাঁরা নিজেরাই এসব উপায়-উপকনণ ও বাতিল পন্থা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছিলেন।
ঈসা ইবনে হামযা বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে হুকাইমের কাছে গেলাম তাঁর বিসর্প (Erysipelas- an inflammation of the skim with redness) রোগ হয়েছিল। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলামঃ আপনি এ রোগের জন্যে কোন তাবীজ-কবজ বাঁধেন না কেন? জবাবে তিনি বললেনঃ
( আরবি******************) আমি তা থেকে আল্লাহর কাছে পানা চাই।
অপর বর্ণনায় তাঁর উক্তি এইঃ ( আরবি******************)
তার অপেক্ষা মৃত্যু অতি নিকটবর্তী যে লোক কিছু একটা ঝুলাবে, বাঁধবে, তাকে তারই ওপর ছেড়ে দেয়া হবে।
হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসঊদ (রা) তাঁর স্ত্রীর কাছে গিয়ে দেখতে পেলেন, তার গলায় কি যেন বাঁধা রয়েছে। তিনি তা টেনে ছিড়ে ফেললেন। পরে বললেনঃ ( আরবি******************)
আবদুল্লাহর বংশের লোকেরা শিরক করা থেকে বিমুখ হয়ে গেছে, যে বিষয়ে আল্লাহ্ কোন দলিল নাযিল করেন নি।
পরে তিনি বললেন, আমি নবী করীম (সা)-কে বলতে শুনেছিঃ ( আরবি******************)
তাবীজ-তুমার, কবজ, তাওলা ইত্যাদি সব শিরক। লোকেরা জিজ্ঞেস করলঃ ‘তাওলা’ কাকে বলে? তিনি বললেন, তা এমন একটা তদবীর ও আমল যা মেয়ে-লোকেরা স্বামীদের বেশি ভালবাসা পাওয়ার জন্যে ব্যবহার করে।
সহজকথায় ‘তাওলা’-ও এক প্রকার যাদু।
আলিমদের মত হচ্ছে, যে সব তাবীজ আরবী ভাষায় লিখিত নয়, তাতে কি লিখিত রয়েছে তা জানা বোঝা যায় না- তাতে যাদুও থাকতে পারে, কুফরি কথাবার্তাও থাকতে পারে। তাই তা নিষিদ্ধ। কিন্তু যদি তার অর্থ ও মর্ম বোঝা যায় এবং তাতে আল্লাহর যিকির বা নাম উল্লেখ থাকে, তবে তা নিষিদ্ধ বা হারাম নয়। এরূপ অবস্থায় তাবীজ দো’আ পর্যায়ে গণ্য। চিকিৎসা নয়, ঔষধও নয়, আল্লাহর সাহায্যের আশা মাত্র। জাহিলিয়াতের যুগে ব্যবহৃত তাবীজে যাদু, শিরক বা রহস্যপূর্ণ কথাবার্তা থাকত, যার কোন অর্থ বোঝা যেত না। এ জন্যে তা হারাম ঘোষিত হয়েছিল।
হযরত ইবনে মাসউদ (রা) তাঁর স্ত্রীকে জাহিলিয়াতের এসব মন্তর ও তাবীজ ব্যবহার করতে নিষেধ করেছিলেন। তিনি জবাবে একটি ঘটনা বর্ণনা করলেন। বললেনঃ আমি একদিন বাইরে বের হলাম, তখন অমুক ব্যক্তি আমাকে দেখে ফেলল। আমার দুই চোখ থেকে অশ্রু ধারা প্রবাহিত হতে শুরু করল।
পরে আমি মন্ত্র পড়লে চোখের পানি বন্ধ হয়ে গেল। মন্ত্র পড়া বন্ধ করলে আবার ফরফর বেগে পানি পড়তে শুরু করে। ইবনে মাসউদ বললেনঃ ( আরবি******************)
এ হচ্ছে শয়তান। তুমি যখন ওকে মেনে নাও, তখন সে তোমাকে ছেড়ে দেয়। আর তুমি যখন তার অবাধ্যতা কর তখন সে তার আঙ্গুলী দিয়ে তোমার চোখে খোঁচা দেয়। কিন্তু তুমি নবী করীম (সা) যা করতেন তাই যদি কর তাহলে তা তোমার জন্যে খুবই ভাল এবং সম্ভবত তুমি নিরাময়তাও লাভ করতে পারবে। তা হচ্ছে, নিজের চোখে পানি দাও এবং বল দো’আ। (ইবনে মাজাহ, আবূ দাউদ)
খারাপ লক্ষণ গ্রহণ
কোন কেন জিনিস থেকে খারাপ লক্ষণ গ্রহণ- তা কোন স্থান, কোন ব্যক্তি বা অন্য যে কোন জিনিস থেকেই হোক, তা ভিত্তিহীন কুসংস্কার ছাড়া আর কিছুই নয়। বহু আগের ও প্রাচীনতম কাল থেকেই তা মানব সমাজে চলে এসেছে এবং আরও বহুকাল অবধি হয়ত তা চলতেও থাকবে। বহু ব্যক্তি ও বহু মানব গোষ্ঠীকেই এর মধ্যে নিমজ্জিত দেখতে পাওয়া যায়। হযরত সালেহ্ নবীর সময়ের লোকেরা বলেছিলঃ ( আরবি******************)
আমাদের মতে তো তুমি এবং তোমার সঙ্গী সাথী খারাপ লক্ষণ বিশেষ।
ফিরাঊন ও তার লোকদের ওপর কোন বিপদ ঘনীভূত হয়ে এলেঃ ( আরবি******************)
তারা মূসা ও তাঁর সঙ্গীদের কুলক্ষণ মনে করতে শুরু করে দিত।
চরম গুমরাহীতে নিমজ্জিত বিপুল সংখ্যক কাফিরের ওপর সেকালে নবী-রাসূলগণের দাওয়াত অস্বীকার করার দরুন যখন কোন বিপদ আপতিত হতো, তখন তারা বলতঃ
( আরবি******************) আমরা তোমাদেরকে কুলক্ষণে মনে করি।
এর জবাবে নবী-রাসূলগণ বলতেনঃ
( আরবি******************)- তোমাদের কুলক্ষণ তো তোমাদের সঙ্গে লেগে আছে।
অর্থাৎ তোমাদের দুর্ভাগ্যের কারণ তোমাদেরই সঙ্গী। আর তা হচ্ছে, তোমাদের কুফরি, আল্লাহর সাথে তোমাদের শত্রুতা এবং আল্লাহ্ ও রাসূলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ।
খারাপ লক্ষণ গ্রহণে জাহিলিয়াতের যুগের আরবদের বিশ্বাস ছিল ভিন্নতর। কিন্তু ইসলাম এসে সেই সবকে বাতিল ঘোঘণা করে এবং তাদের চালিত করে সুদৃঢ় ও বিবেক বুদ্ধিসম্মত পথে।
নবী করীম (সা) কুলক্ষণ গ্রহণকে গণকদারী ও যাদুক্রিয়ার সাথে একই সুত্রে গেঁথেছেন। তিনি বলেছেনঃ ( আরবি******************)
যে লোক নিজে কুলক্ষণ গ্রহণ করবে বা যার জন্যে কুলক্ষণ গ্রহণ করা হবে বা গণনা করা হবে কিংবা যাদু করবে যার জন্যে যাদু করা হবে সে আমার উম্মতের মধ্যে গণ্য নয়। (তিবরানী)
তিনি আরও বলেছেনঃ ( আরবি******************)
রমল, পাখির উড়ানো কুলক্ষণ গ্রহণ ও পাথরকুচি নিক্ষেপ করে খারাপ লক্ষণ গ্রহণ- এ সবই কুসংস্কার বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত।
এ কুলক্ষণ গ্রহণ কোন জ্ঞান-বুদ্ধির ওপর ভিত্তিশীল নয়। এর সাথে বাস্তবতারও কোন সম্পর্ক নেই। এটা মানুষের বিবেক-বুদ্ধি, চিন্তাশক্তি ও মানসিক দুর্বলতার ফসল। কুসংস্কারাচ্ছন্ন মন-মানসিকতার দরুনই মানুষ লক্ষণ- তা কু হোক বা শুভদ্বারা চালিত হতে প্রস্তুত হয়ে থাক। নতুবা কোন বিশেষ ব্যক্তিকে, কোন নির্দিষ্ট স্থানকে কিংবা গ্রহ-তারকার কোন কক্ষে প্রবেশ করাকে কুলক্ষণের প্রতীক মনে করার কি অর্থ থাকতে পারে? কোন পাখির আওয়াজ শুনলেই যাত্রা অশুভ হয়ে যাবে কিংবা চোখের পাতার কম্পনে ভাল বা মন্দ নিহিত থাকবে অথবা কোন বিশেষ শব্দ শুনলেই সমস্ত সংকল্প নড়বরে হয়ে যাবে, এমন কথার সাথে সুস্থ বিবেক-বুদ্ধির কোন সম্পর্ক থাকতে পারে না।
আসলে মানুষের ভিতরে স্বভাবগতভাবে নিহিত দুর্বলতার দরুনই কোন কোন জিনিস থেকে ‘লক্ষণ’ গ্রহণ করে। অতএব বুদ্ধিমান সচেতন মানুষের কর্তব্য কোনরূপ দুর্বলতার কাছে মাথা নত না করা।
একটি মরফু হাদীসে বলা হয়েছেঃ ( আরবি******************)
তিনটি জিনিস এমন রয়েছে, যা থেকে খুব কম লোকই রক্ষা পেতে পারে। তা হচ্ছেঃ কুধারণা, কুলক্ষণ গ্রহণ এবং হিংসা। অতএব তোমার মনে যদি কুধারণা জাগে, তাহলে তুমি তাতে প্রত্যয় নিও না, কুলক্ষণ যদি তোমার মনে দ্বিধার সৃষ্টি করে, তাহলে মাঝপথ থেকে ফিরে যেও না। আর যদি হিংসার উদ্রেক হয়, তাহলে তুমি তেমনটা চাইবে না। (তিবরানী)
রাসূলের শেখানো এই পদ্ধতির অনুসরণ করা হলে এ তিনটি মনের পটেই জেগে উঠা ভিত্তিহীন চিন্তা-কল্পনা ও শয়তানের ওয়াসওয়াসা ছাড়া আর কিছুই মনে হবে না এবং বাস্তব কাজের ওপর তার কোন প্রভাব প্রতিফলিত হবে না। এরূপ অবস্থায় আল্লাহ্ তা’আলা এসব ক্ষমা করে দেবেন। হযরত ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম (সা) ইরশাদ করেছেনঃ ( আরবি******************)
কুলক্ষণ গ্রহণ শিরক, কুলক্ষণ গ্রহণ শিরক, কুলক্ষণ গ্রহণ শিরক।
ইবনে মাসউদ বলেছেনঃ আমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যার মনে কুলক্ষণ সংক্রান্ত চিন্তার উদ্রেক হয় না। কিন্তু আল্লাহর ওপর নির্ভরতা গ্রহণ করলে এ ধরনের ভাবধারা সবই নিঃশেষ হয়ে যায়। (আবূ দাউদ, তিরমিযী)
জাহিলী অন্ধ অনুসরণের বিরুদ্ধে জিহাদ
ইসলাম যেভাবে জাহিলী আকীদা-বিশ্বাস ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে,- কেননা এগুলো বিবেক-বুদ্ধি, নৈতিকতা ও সুস্থ আচার-আচরণের পরিপন্থী, অনুরূপভাবে জাহিলিয়াতের অন্ধ অনুকরণ-অনুসরণের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছে। কেননা তা হিংসা-বিদ্বেষ, অহংকার-গৌরব ও গোত্রীয় আত্মাভিমানের ওপর ভিত্তিশীল।
বিদ্বেষমূলক ভাবধারা ইসলামের বিপরীত
এ পর্যায়ে ইসলাম সর্বপ্রথম বিদ্বেষমূলক ভাবধারার ওপর কুঠারাঘাত করেছে এবং তার সব রূপ ও ধরনকে মাটির তলায় দাফন করেছে। সেই সাথে বিদ্বেষাত্মক ভাবধারা সৃষ্টি ও তার দিকে জনগণকে আহ্বান করাকে হারাম ঘোষণা করেছে। নবী করীম (সা) উদার কণ্ঠে ঘোষণা করেছেনঃ ( আরবি******************)
যে লোক বিদ্বেষাত্মক ভাবধারার দিকে লোকদের আহ্বান জানায়, যে লোক বিদ্বেষাত্মক ভাবধারার ওপর লড়াই করে এবং যে লোক বিদ্বেষাত্মক ভাবধারা নিয়ে মরে, তারা কেউই আমার উম্মতের মধ্যে গণ্য নয়। (আবূ দাঊদ)
অতএব ইসলামের দৃষ্টিতে চামড়ার বিশেষ বর্ণের কোন গুরুত্ব বা বিশেষত্ব নেই, লোকদের বিশেষ কোন জাতির প্রাধান্য স্বীকৃত নয়। পৃথিবীর কোন ভুখণ্ডেরও বিশেষত্ব নেই অপরাপর অংশের ওপর। কোন বর্ণের পক্ষেও অপর বর্ণের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ সৃষ্টি করা মুসলমানের জন্যে হালাল নয়। কোন জাতির ওপর অপর জাতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠারও কোন অধিাকর নেই। বিশেষ বিশেষ অঞ্চল বা রাজ্য-সম্রাজ্য সম্পর্কেও ইসলামের এ কথা। বর্ণে-বংশে-জাতিতে-অঞ্চলের পার্থক্যের ভিত্তিতে মানুষের মধ্যে কোন পার্থক্য করতে ইসলাম আদৌ প্রস্তুত নয়। অতএব মুসলমান বর্ণ, জাতি বা দেশভিত্তিক হিংসা-বিদ্বেষের ভিত্তিতে কোন কাজ করতে পারে না। আর ন্যায়-অন্যায়, সত্য-অসত্য, জুলুম-ইনসাফ- সর্বাবস্থাই নিজ জাতির সমর্থন করে যাওয়াও কোন মুসলমানের কর্ম নয়। ওয়াসিলা ইবনে আসকা (রা) বলেনঃ ( আরবি******************)
আমি বললাম, ইয়া রাসূল, ‘আসবিয়াত’ কাকে বলে? জবাবে তিনি বললেনঃ তোমার জাতি জুলুমের ওপর হওয়া সত্ত্বেও তুমি তার সাহায্য-সহযোগিতা করবে, এটাই ‘আসবিয়াত’ (বিদ্বেষাত্মক ভাবধারা অপর জাতির বিরুদ্ধে।
আল্লাহ্ তা’আলার ঘোষণা হচ্ছেঃ ( আরবি******************)
হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা ইনসাফ ও সুবিচারের জন্যে দাঁড়িয়ে যাও। আল্লাহর সাক্ষ্যদাতা হয়ে- যদিও তা তোমাদের নিজেদের পিতামাতার ও নিকটাত্মীয়দের বিরুদ্ধেই হোক। (সূরা নিসাঃ ১৩৫)
( আরবি******************) কোন বিশেষ জাতির শত্রুতা যেন তোমাকে অবিচার করতে প্রবৃদ্ধ না করে।
নবী করীম (সা)-এর সুবিচার নীতি এ অর্থেই জাহিলিয়াতের যুগে সর্বত্র বিস্তীর্ণ ছিল, তা বাহ্যিক অর্থেই গৃহীত। তিনি বলেছেনঃ ( আরবি******************)
তুমি তোমার ভাইয়ের সাহায্য কর, সে জালিম হোক, কি মজলুম।
উত্তরকালে সাহাবীদের মধ্যে ইসলামী ঈমান যখন দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হলো তখন উপরিউক্ত কথাটির খারাপ অর্থ লোকদের সম্মুখে ভেসে উঠল এবং তদ্দরূন তাদের মনে আতঙ্ক ও বিস্ময় জেগে উঠল। তাঁরা প্রশ্ন করলেনঃ ( আরবি******************)
হে রাসূল! আপনার কথানুযায়ী আমার ভাই মজলুম হলে তাকে তো সাহায্য করতে পারি এবং এ পর্যায়ে আপনার কথার তাৎপর্য বুঝতে পারি। কিন্তু সে জালিম হলে তাকে আমরা কিভাবে সাহায্য করতে পারি?- এ কথাটির অর্থ বুঝতে পারি নি। জবাবে তিনি বললেনঃ ( আরবি******************)
তুমি তাকে জুলুম থেকে বিরত রাখবে আর এটাই তাকে সাহায্য করতে বলার অর্থ।
এ থেকে আমরা স্পষ্ট জানতে পারি যে, মুসলিম সমাজে কোন আঞ্চলিক শ্রেষ্ঠত্বের দাবি কিংবা কোন জাতীয়তার শ্রেষ্ঠত্বের দাবি চলতে পারে না। দেশ মাতৃকার দোহাই বা আঞ্চলিক কিংবা শ্রেণী-বংশ-বর্ণ ভাষা-ভিত্তিক জাতীয়তার দোহাই ও আত্মম্ভরিতা জাহিলিয়াতের দাবি। এর সাথে ইসলাম, রাসূল বা আল্লাহর কিতাবের কোনই সম্পর্ক থাকতে পারে না।
বস্তুত ইসলাম তার আকীদা পরিপন্থী কোন বন্ধুতা-সংস্থা বা ইসলামী ভ্রাতৃত্বের বাইরে কোন ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক সমর্থন করে না। ঈমান ও কুফর ভিন্ন মানুষে-মানুষে পার্থক্য করার অপর কোন ভিত্তিকেও ইসলাম স্বীকার করে না। অতএব ইসলামের শত্রু- কাফির মুসরমানেরও শত্রু, সে তার স্বদেশী, স্বজাতীয় ও প্রতিবেশী হলেও। শুধু তা-ই নয়, তার আপন ভাই, পিতা, জননী যেই হোক, সেও তার আপন নয়, যদি ইসলামের দুশমন হয়। আল্লাহ্ তা’আলা এ কথাই বলেছেন নিম্নের এ আয়াতেঃ ( আরবি******************)
আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি ঈমানদার জাতিকে আল্লাহ্ ও রাসূলের শত্রুদের সাথে বন্ধুত্ব পোষণকারী রূপে পাবে না, তারা তাদের পিতা, পুত্র, ভাই ও বংশীয় লোকই হোক না কেন। (সূরা মুজাদালাঃ ২২)
বলেছেনঃ ( আরবি******************)
হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা তোমাদের পিতৃস্থানীয় লোক ও ভাই সদৃশ লোকদের বন্ধু, পৃষ্ঠপোষক রূপে গ্রহণ করবে না, যদি তারা ঈমানের ওপর কুফরিকে অগ্রাধিকার দেয়। (সূরা আত্ তাওবাঃ ২৩)
বংশ ও বর্ণের কোন গৌরব নেই
বুখারী শরীফে বর্ণিত হয়েছে, হযরত বিলাল হাবশী ও আবূ যর গিফারী (রা) দুজনেই প্রাথমিক কালের সাহাবী। দুজন পরস্পরের ওপর ক্রোধান্ধ হয়ে গালাগাল করতে শুরু করেন। ক্রোধের তীব্রতায় হযরত আবূ যর (রা) হযরত বিলাল (রা)-কে সম্বোধন করে বললেনঃ ( আরবি******************)- ‘হে কালোর পুত্র’। হযরত বিলাল নবী করীম (সা)-এর কাছে এ কথা বলে অভিযোগ করলেন। তিনি হযরত আবূ যরকে বললেনঃ ( আরবি******************)
তুমি ওর মাকে মন্দ বললে? দেখা যায় তোমার মধ্যে জাহিলিয়াতের স্বভাব-চরিত্র এখনও অবশিষ্ট কয়েছে।
হযরত আবূ যর (রা) থেকেই বর্ণিত, নবী করীম (সা) তাঁকে বলেছেনঃ ( আরবি******************)
তুমি নিজ সম্পর্কে ভেবে দেখ। লাল বা কালো বর্ণের লোকদের অপেক্ষা তুমি কোন অংশেই উত্তম ব্যক্তি নও। তুমি ওর ওপর কেবল মাত্র তাক্ওয়ার ভিত্তিতেই শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে পার। (আহমদ)
নবী করীম (সা) বলেছেনঃ ( আরবি******************)
তোমরা সকলেই আদমের সন্তান। আর আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে মাটি দিয়ে।
এ সবের সাহায্যে মুসলমানের বংশ বর্ণ পিতৃপুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদার ভিত্তিতে গৌরব করা ও অন্যদের তুলনায় নিজেদের বড়ত্ব প্রমাণ করতে চেষ্টা করাকে ইসলাম সম্পূর্ণ হারাম করে দিয়েছে। কেননা এগুলোই হচ্ছে জাহিলিয়াতের উপকরণ। নিতান্ত লালসার দাসত্ব করতে গিয়েই মানুষ এ কাজ করতে পারে। কাজেই আমি অমুকের ছেলে, আমি অমুকের বংশধর আর তুমি অমুক হীন বংশের লোক, আমি শ্বেতকর্ণ, আর তুমি কৃষ্ণাঙ্গ, আমি আরব আর তুমি অনারব ইত্যাদি ধরনের বিদ্বেষাত্মক ও হিংসাত্মক কথাবার্তা পরস্পরে বলার কোন অবকাশ ইসলামে নেই।
বস্তুত সমস্ত মানুষ যখন এক ও অভিন্ন মূল থেকে উৎসারিত, তখন পরবর্তী লোকদের পক্ষে বংশ গোত্র বা রক্ত নিয়ে গৌরব করার ও অপরের তুলনায় নিজের শ্রেষ্ঠত্ব দেখানর কোন অর্থ হয় না, তার অধিকারও কারো থাকতে পারে না। বংশের কোন গুরুত্ব আছে যদি ধরেও নেয়া যায়, তবু তার বংশে জন্মগ্রহণকারী ব্যক্তির নিজের কি শ্রেষ্ঠত্ব থাকতে পারে বা তার কি অপরাধ মনে করা যেতে পারে? নবী করীম (সা) ওজস্বিনী কণ্ঠে ঘোষণা করেছেনঃ ( আরবি******************)
তোমাদের এসব বংশ নিয়ে অপরের ওপর কোন শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করতে পার না। কেননা তোমরা সমস্ত মানুষই আদমের সন্তান- বংশধর। দ্বীনদারী ও আল্লাহ্ ভীতি ছাড়া তোমাদের কারো কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই অপর লোকদের ওপর। (আহমদ)
তিনি আরও বলেনঃ ( আরবি******************)
সমস্ত মানুষই তো আদম-হাওয়ার বংশধর। কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তোমাদের বংশ বা আভিজাত্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন না। আসলে তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সবচেয়ে মর্যাদাবান সে, যে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে আল্লাহ্ ভীরু।
বাপ-দাদার বা বংশের উচ্চতা নিয়ে গৌরবকারী লোকদেরকে কঠোর ভাষায় সাবধান করে দিয়ে নবী করীম (সা) বলেছেনঃ
হে লোকেরা! বাপ-দাদাদের নিয়ে গৌরব করা ত্যাগ কর-সেসব বাপ-দাদা যারা মরে জাহান্নামের কয়লা হয়ে গেছে। নতুবা তারা পোকা-মাকড়ের তুলনায়ও অধিক দীন ও লাঞ্ছিত হবে। আল্লাহ্ তা’আলা জাহিলিয়াতের আত্মম্ভরিতা ও বংশ গৌরব নির্মূল করে দিয়েছেন। এক্ষণে মানুষ হয় মুমিন মুত্তাকী হবে অথবা হবে পাপী দুশ্চরিত্র। সব মানুষই আদমের সন্তান। আর আদম মাটি থেকে সৃষ্ট। (আবূ দাউদ, তিরমিযী, বায়হাকী)
এ হাদীসে বড় গুরুত্বপূর্ণ দিক্ষা রয়েছে তাদের জন্যে, যারা নিজেদের প্রাচীন বাপ-দাদা পূর্ববংশ, আবরী-আজমী জাহিলিয়াতের অগ্রনায়ক ফিরাউন ও কাইজার কিসরাকে নিয়ে গৌরব করে অথচ নবী করীমের ঘোষণার দৃষ্টিতে তারা জাহান্নামের কয়লা ছাড়া আর কিছুই নয়।
হুজ্জাতুল বিদা’র সময় হজ্জের মাসে সম্মানিত মক্কা নগরে লক্ষাধিক মুসলিম সমবেত হয়ে রাসূলে করীমের উদাত্ত ভাষণ শুনছিলেন। তিনি শুরুতেই ঘোষণা করলেনঃ ( আরবি******************)
হে জনগণ! তোমাদের আল্লাহ্ এক। কোন আরববাসীর কোন শ্রষ্ঠত্ব নেই কোন অনারবের ওপর, কোন অনারবের কোন শ্রেষ্টত্ব নেই কোন আরবের ওপর। লাল-ধলা বর্ণের লোকের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই কালো বর্ণের লোকের ওপর। কালো বর্ণের লোকেরও কোন শ্রেষ্ঠত্ব-বৈশিষ্ট্য নেই লাল-ধলা লোকদের ওপর তাকওয়া ছাড়া। আল্লাহর ঘোষণা হচ্ছে, তোমাদের মধ্যে সেই লোক আল্লাহর কাছে অধিক মর্যাদাবান, যে তোমাদের মধ্যে অধিক আল্লাহ্-ভীতি সম্পন্ন। (বায়হাকী)
মৃতের জন্যে বিলাপ
ইসলাম জাহিলিয়াত যুগের যেসব আচার-আচরণের অনুকরণের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে তন্মধ্যে একটি হচ্ছে, মৃত ব্যক্তি সম্পর্কে জাহিলিয়াতের আচরণ।
মৃতের জন্যে বিলাপ করা, খুব বেশি দুঃখ ও মনোকষ্ট প্রকাশে বাড়াবাড়ি করা তার মধ্যে অন্যতম।
ইসলাম তার অনুসারীদের শিক্ষা দিয়েছে যে, মৃত্যু এক জগত থেকে আর এক জগতে যাত্রা করা বা স্থানান্তর গ্রহণ ভিন্ন আর কিছুই নয়। তা কোন চূড়ান্ত ধ্বংস, বিনাশ ও বিলুপ্তি নয়। উপরন্তু বিলাপ করলেই মৃত জীবন্ত হয়ে যাবে না। আল্লাহর ফয়সালা বদলে যাবে না অন্য কোন ফয়সালার দরুন। অতএব মুমিনের কর্তব্য হচ্ছে, প্রতিটি বিপদকে যেমন ধৈর্য সহকারে মুকাবিলা করতে হয়, মৃত্যুর ব্যাপারেও তারা তেমনি ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা অবলম্বন করবে। তা থেকে বরং সবক গ্রহণ করবে। মনে মনে এ আশা পোষণ করবে যে, আল্লাহর শিখান উক্তি বারবার বলবেঃ ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন- ‘আমরা আল্লাহরই জন্যে এবং আমরা তাঁরই কাছে ফিরে যাব।’
তাই জাহিলিয়াতের যুগে মৃতের জন্যে যে বিলাপ করা হতো, ইসলামে তা হারাম- পরিত্যাজ্য। রাসূলে করীম (সা) তা থেকে নিঃসম্পর্কতার কথা ঘোঘণা করেছেন। তিনি বলেছেনঃ ( আরবি******************)
যে লোক মৃতের জন্যে বিলাপ করতে গিয়ে নিজের মুখমণ্ডল আহত করে, পরনের কাপড় ছিন্নভিন্ন করে ও জাহিলিয়াতের ন্যায় চিৎকার আর্তনাদ করে, সে আমার উম্মতের মধ্যে গণ্য নয়। (বায়হাকী)
মৃতের জন্যে শোক করতে গিয়ে মাতামী পোশাক পরা, অলংকারাদি পরিহার করা ও সাধারণ পরিধেয় ত্যাগ করা এবং আকার-আকৃতিতে পরিবর্তন সাধন করা কোন মুসলমানের জন্যে হালাল বা জায়েয নয়। তবে স্বামীর মৃত্যুতে স্ত্রীর জন্যে যা করণীয়, তা অবশ্য করতে হবে। যেমন চার মাস দশদিন ইদ্দত পালন করা তার কর্তব্য। স্বামীর জন্যে স্ত্রীর এ বিধিবদ্ধ শোককাল এটা দাম্পত্য জীবন অবসানের কারণে কর্তব্য। তাদের দুজনের মধ্যে যে প্রেম-প্রীতির বন্ধন ছিল, স্বামীর মৃত্যুতে তা ছিন্ন হয়ে গেল বলে তার এতটুকু শোক প্রকাশ করা উচিত। তাতে সেই পবিত্র সম্পর্কের প্রতিই সম্মান প্রদর্শন করা হয়। কাজেই এ সময় তার কোন অলংকার ব্যবহার করা উচিত নয়, যেন ইদ্দত যাপন কালে বিবাহেচ্ছু বহু লোকের দৃষ্টিতে আকর্ষণীয়া হয়ে না উঠে।
কিন্তু মৃত ব্যক্তি স্বামী ছাড়া অন্য কেউ হলে- যেমন পিতা, ভাই, পুত্র, মা ইত্যাদি তিন দিনের বেশিকাল শোক প্রকাশ করা স্ত্রীলোকদের জন্যে জায়েয নয়। যয়নব বিনতে আবূ সালমা থেকে বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে, তিনি নবী করীমের বেগম উম্মে হাবীবা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, তাঁর পিতা আবূ সূফিয়ান ইবনে হারম মারা গেলে এবং যয়নব বিনতে জাহাশের ভাই মারা গেলে তাঁরা দুজনই সুগন্ধি ব্যবহার করলেন এবং বললেনঃ সুগন্ধি লাগাবার এখন কোন প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু নবী করীম (সা) বলেছেনঃ ( আরবি******************)
যে নরী আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাসী, তার পক্ষে মৃতের জন্যে তিন রাতের অধিক শোক করা জায়েয নয়। তবে স্বামীর জন্যে শোক করতে হবে চার মাস দশদিন পর্যন্ত। (বুখারী)
স্বামীর জন্যে এই শোক ওয়াজিব। এর প্রতি অবজ্ঞা দেখানো চলবে না। একজন মহিলা নবী করীমের খেদমতে হাযির হয়ে বলল, আমার মেয়ের স্বামী মরে গেছে। এখন কি আমি তার চোখে সুরমা লাগাতে পারি? নবী করীম (সা) বললেনঃ না, দুবার তিনবার এই একই জবাব দিলেন। এ কথা দ্বারা স্পষ্ট বোঝা গেল, স্বামী মরে গেলে স্ত্রীকে সৌন্দর্যের উপকরণাদি ও অলংকার ব্যবহার করা ইদ্দত কাল শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়ের জন্যে হরাম।
তবে কোন রূপ অস্থিরতা প্রকাশ ছাড়া শুধু শোক বা দুঃখ করা এবং চিৎকার না করে কান্নাকাটি করা- এ তো স্বাভাবিক ব্যাপার। এজন্যে কোন গুনাহ্ হবে না। হযরত উমর (রা) শুনতে পেলেন, খালিদ ইবনে ওয়ালীদের জন্যে মেয়েরা কান্নাকাটি করছে। তখন কোন কোন পুরুষ তাদের নিষেধ করার ইচ্ছা করল। তা দেখে হযরত উমর (রা) বললেনঃ ( আরবি******************)
ছেড়ে দাও ওদের। ওরা আবূ সুলায়মান- খালিদের জন্যে কান্নাকাটি করুক, যতক্ষণ না মাথায় মাটি তুলছে বা উচ্চস্বরে চিৎকার করছে।
পারস্পরিক কার্যাদি
আল্লাহ্ তা’আলা মানুষকে এমন প্রকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন যে, তারা পরস্পরের কাছে ঠেকা, পরস্পরের সাহায্যের ওপর একান্তভাবে নির্ভরশীল। প্রত্যেক ব্যক্তির যা কিছু প্রয়োজন তা যোগাড় করা তার একার পক্ষে কখখনই সম্ভবপর হয় না। কেউ হয়ত কোন জিনিসের অধিকারী, যা অপর কারো প্রয়োজন পূরণ করে এবং কেউই হয়ত এমন জিনিসের মুখাপেক্ষী যা অপর কারো কাছে পাওয়া যায়। এ করণে আল্লাহ্ তা’আলা তাদের মধ্যে ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে পণ্য ও মুনাফা বিনিময় করণের ব্যবস্থা মেনে চলার ভাবধারা জাগিয়ে দিলেন। এভাবেই মানুষের যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ হয়ে থাকে এবং এ করেই মানব জীবন দৃঢ়তা লাভ করে। এ শুধু ব্যক্তিগণের পারস্পরিক ব্যাপারই নয়, জাতি ও রাষ্ট্রসমূহও পারস্পরিক কল্যাণ ও উৎপাদনের ফসল বিনিময় করে চলতে পারে।
নবী করীম (সা) যখন প্রেরিত হলেন তখন আরব সমাজে নানা প্রকারের ক্রয়-বিক্রয় ও পারস্পরিক লেন-দেন চলছিল। তখন ইসলামী শরীয়তের অনুকূল ব্যবস্থা ও কার্যাদি চালু রাখা হলো, তা জায়েয বলে ঘোষিত হলো, এবং যা যা শরীয়তের পরিপন্থী ছিল, তা সবই হারাম ও নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলো। এ নিষেধ কয়েক পর্যায়ে বিভক্ত। যেমন কোন গুনাহের কাজে, ধোঁকা-প্রতারণার কাজে, অধিক মূল্য ও মুনাফা লুণ্ঠনের কাজে এবং চুক্তির পক্ষদ্বয়ের মধ্যে কোন এক পক্ষের ওপর জুলুম হওয়ার কাজে সাহায্য ও সহযোগিতা করা।
হারাম জিনিস বিক্রয় করা হারাম
ক. নিষিদ্ধ ও হারাম ঘোষিত দ্রব্যাদি ব্যবহার করা ও তা থেকে উপকার গ্রহণও হারাম এবং গুহান পর্যায়ের কাজ। এ কারণে তা ক্রয় বা বিক্রয় করা কিংবা তার ব্যবসা করা হারাম। শূকর, মদ্য, হারাম খাদ্য-পানীয়, মূর্তি, ক্রুশ, প্রতিকৃতি (Statue) প্রভৃতি এ পর্যায়ে গণ্য। এসব জিনিসের ক্রয়-বিক্রয় ও ব্যবসা যদি জায়েয করে দেয়া হতো তাহলে গুনাহের এসব কাজ ব্যাপক প্রসারতা লাভ করত। জনগণকে সেই কাজে উদ্বুদ্ধ করা হতো, তা করার জন্যে সহজতার সৃষ্টি করা হতো, লোকদের তার কাছে নিয়ে যাওয়া হতো। সেজন্যে লোকদের উৎসাহিত করা হতো। কিন্তু যেহেতু এসব জিনিসের ক্রয়-বিক্রয় ও তা অর্জন হারাম করে দেয়া হয়েছে। ফলে মানুষ এসব থেকে বেঁচে থাকতে পারে। এক্ষণে এসব জিনিসের দিকে লোকদের না দৃষ্টি পড়তে পারে, না তা স্মরণ করার কোন কারণ ঘটতে পারে। এসব জিনিসের সংস্পর্শ থেকেই মানুষকে দূরে সরিয়ে রাখতে চাওয়া হয়েছে। এজন্যেই নবী করীম (সা) বলেছেনঃ ( আরবি******************)
আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল মদ্য, মৃত জীব, শূকর ও মূর্তি বিক্রয় করা হারাম করে দিয়েছেন। (বুখারী, মুসলিম)
এক হাদীসে বলা হয়েছেঃ ( আরবি******************)
আল্লাহ্ যখন কোন জিনিস হারাম করেন তখন সে জিনিসের বিক্রয় মূল্যও হারাম করে দেন। (আহমদ, আবূ দাউদ)
ধোঁকাপূর্ণ বিক্রয় হারাম
খ. যে ধরনের বিক্রয়ে পণ্য অজ্ঞাত বা ধোকা হওয়ার কিংবা এক পক্ষ কর্তৃক অপর পক্ষকে ক্ষতি সাধনের সুযোগের কারণে পারস্পরিক ঝগড়া হওয়ার আশংকা থাকে, তা ‘কারণ বন্ধের’ নীতি অনুযায়ী নিষিদ্ধ। যেমন পুরুষ উষ্ট্রের পৃষ্ঠের যে জিনিস বা উষ্ট্রী গর্ভে যে বাচ্চা রয়েছে, তা বিক্রয় করা কিংবা উড়ন্ত পাখি বা পানির মধ্যে অবস্থিত মাছ অথবা এ ধরনের অজানা পণ্য ক্রয় ও বিক্রয় করা।
নবী করীম (সা)-এর সময়ে ক্ষেতের ফসল বা বাগানের ফল পাকার পূর্বেই বিক্রয় করে দেয়া হতো। বিক্রায় সাব্যস্ত হওয়ার পর অনেক সময় নৈসর্গিক কারণে ফল ধ্বংস হয়ে যেত, ফসল বিনষ্ট হতো, ফলে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে ঝগড়ার সৃষ্টি হতো। বিক্রয়কারী বলত, আমি তো বেঁচে দিয়েছে। ক্রেতা বলত, যে ফল বিক্রয় করেছ, সেই ফল-ই নেই। এ কারণে নবী করীম (সা) ফল-ফসল পাঁকার পূর্বে বিক্রয় করতে স্পষ্ট ভাষায় নিষেধ করেছেন। তবে সঙ্গে সঙ্গে ফল কাটা সাব্যস্ত হলে তা জায়েয হতে পারে। শস্যের মঞ্জরী বা শিষ সাদা হওয়া ও বিপদমুক্ত হওয়ার পূর্বে বিক্রয় করতেও নিষেধ করা হয়েছে। তিনি বলেছেনঃ ( আরবি******************)
তোমরা কি চিন্তা করেছ, আল্লাহই যখন ফল বন্ধ করে দিলেন, তখন তোমাদের ভাইর টাকা লওয়া তোমাদের জন্যে কিভাবে জায়েয হতে পারে?
অজ্ঞাত পণ্য মাত্রই যে ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ এমন কথা নয়। কোন কোন ব্যাপারে পণ্যের অনেকাংশ অজানা অন্ধকারে থেকে যায়। যেমন কেউ যদি কোন পাকা বাড়ি ক্রয় করে, তাহলে তার ভিত্তি ও প্রাচীরসমূহের ভিতরকার অবস্থা ক্রেতার অগোচরেই থেকে যায়। সে বিষয়ে কিছু জানা তার পক্ষে সম্ভবপর হয় না। কিন্তু তার অন্যান্য সবদিকই ক্রয়কারী ভাল করে দেখতে পারে। কাজেই যে জিনিস সম্পূর্ণরূপে অজানা, যার কারণে পরস্পরে ঝগড়া বিবাদ হতে পারে কিংবা যার মধ্যে বাতিল পন্থায় লোকদের মাল ভক্ষণ করার অবকাশ থাকে, তা-ই নিষিদ্ধ।
যদি কোন জিনিস সামান্যভাবে অজানা হয়, আর এ আংশিক অজানা জিনিসের ক্রয়-বিক্রয়ের রেওয়াজ থাকে, তাহলে তার ক্রয়-বিক্রয় যথা মূলা, গাজর, পিয়াজ প্রভৃতি কাকই ও ফুটি-তরমুজের ক্ষেত বিক্রয়। ইমাম মালিকের মতে প্রয়োজনের কারণে তা জায়েয। কেননা তাতে অজ্ঞানতার ক্ষেত্র খুব ব্যাপক নয়, অতি সাধারণ এবং সামান্য।
ইমাম ইবনে তাইমিয়া বলেছেন, ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপারে ইমাম মালিকের নীতি অন্যান্যের নীতির তুলনায় উত্তম কেননা তাঁর নীতি সায়ীদ ইবনুল মুসাইয়্যিবের মতের ওপর ভিত্তিশীল। আর ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত বিষয়াদিতে তিনি বড় ফিকাহবিদ বলে মান্য। ( আরবি******************)
ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের মতও এরই কাছাকাছি।
দ্রব্যমূল্য লয়ে খেলা করা
ইসলাম বাজার ও দ্রব্যমূল্য স্বাভাবিক গতিতে চলতে দিতে ইচ্ছুক। হাট-বাজার স্বাভাবিকভাবে চলতে পারলেই দ্রব্যমূল্য আপনা থেকেই নিয়ন্ত্রিত হতে থাকে, বাজারে পণ্য আমদানী ও তার চাহিদা অনুপাতে দ্রব্যমূল্যে উত্থান-পতন হতেই থাকে। আমরা নবী করীমের যুগে তাই দেখতে পাই। তখন দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেলে লোকেরা এসে বললঃ ইয়া রাসূল, আমাদের জন্যে দ্রব্যমূল্য নির্ধারিত করে দিন। তখন নবী করীম (সা) বললেনঃ ( আরবি******************)
প্রকৃতপক্ষে দ্রব্যমূল্য নির্ধারণকারী হচ্ছে স্বয়ং আল্লাহ্ তা’আলাই। তিনিই মূল্য বৃদ্ধি করেন, তিনি সস্তা করেন। রিযকদাতা তিনিই। আমি তো আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করতে চাই এ অবস্থায় যে, কোনরূপ জুলুম, রক্তপাত বা ধন-মালের অপহরণ ইত্যাদির দিক দিয়ে আমার ওপর দাবিদার কেউ থাকবে না। (আহমদ, আবূদাঊদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)
নবী করীম (সা) এ হাদীসের মাধ্যমে ঘোষণা করেছেন যে, ব্যক্তি স্বাধীনতার ওপর কোনরূপ প্রয়োজন ছাড়াই হস্তক্ষেপ বা নিয়ন্ত্রণ চাপান জুলুম এবং সেই জুলুম থেকে মুক্ত ও পবিত্র থেকেই তিনি আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করতে চান।
কিন্তু বাজারদরের ওপর যদি অস্বাভাবিক অবস্থায় চাপ আসে, যেমন প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি মজুদকরণ শুরু হয়ে যায় এবং মজুদদাররা দ্রব্যমূল্য নিয়ে খেলা করতে শুরু করে, তাহলে সমষ্টির কল্যাণ স্বার্থে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ করে দিতে হবে। তাতে অধিক মূল্য গ্রহণকারীর শোষণ থেকে জনগণকে বাঁচান সম্ভবপর হবে।
অতএব উপরিউক্ত হাদীসের অর্থ এই নয় যে, যে কোন পরিস্থিতিতেই দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ জুলুম ও তা নিষিদ্ধ- লোকদের কষ্ট দূর করা বা সুস্পষ্ট জুলুম থেকে লোকদের বাঁচানর জন্যে হলেও। বরং ইসলামের বিশেষজ্ঞগণ বলেছেন, মূল্য নির্ধারণ দুরকমের হয়। এক প্রকারের মূল্য নির্ধারণে লোকদের ওপর জুলুম হয় এবং তা হারাম। আর এক অবস্থায় মূল্য নির্ধারণ সুবিচার ও ন্যায়পরতার দাবি তা অবশ্যই জায়েয এবং জরুরী।
অতএব অন্যায়ভাবে লোকদের ওপর যদি এমন মূল্য চাপিয়ে দেয়া হয় যাতে তারা রাজি নয়, কিন্তু মুবাহ জিনিস থেকে জনগণকে বিরত রাখা হয়, তাহলে তা হবে হারাম। পক্ষান্তরে লোকদের মধ্যে সুবিচার ও ইনসাফ কার্যকর করার উদ্দেশ্যে যদি মূল্য নির্ধারিত করে দেয়া হয়- প্রচলিত দামে (standardprice) বিক্রয় করতে বাধ্য করা হয় কিংবা প্রচলিত বিনিময় মূল্যের অধিক গ্রহণ থেকে তাদের বিরত রাখা হয়, তাহলে তা করা শুধু জায়েযই নয়, ওয়াজিবও।
প্রথম অবস্থার প্রেক্ষিতে প্রথমোক্ত হাদীসটি উদ্ধৃত। কাজেই লোকরা যখন প্রচলিত নিয়মে কোনরূপ জুলুম ও বাড়াবাড়ি ব্যতীতই দ্রব্য বিক্রয় করে ও পণ্যদ্রবের স্বল্পতার বা জনসংখ্যা বৃদ্ধির করণে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায়, তাহলে গোটা ব্যাপারটাই আল্লাহর উপর সোপর্দ করা কর্তব্য। এরূপ অবস্থায় সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যে বিক্রয় করতে বাধ্য করা অকারণ বাড়াবাড়ি বৈ কিছু নয়।
আর দ্বিতীয় অবস্থায়- লোকদের প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও ব্যবসায়ীরা যদি পণ্যদ্রব্য বিক্রয় না করে অথবা চলতি মূল্যের অধিক দাবি করে, এরূপ অবস্থায় প্রচলিত দামে দ্রব্য বিক্রয় করাও ওয়াজিব। এ সময় দ্রব্য মূল্য নির্ধারিত করে দেয়ার অর্থ, প্রচলিত দাম লোকদের জন্যে বাধ্যতামূলক করে দেয়া। এরূপ অবস্থায় দ্রব্যমূল্য নির্ধারণের অর্থ, আল্লাহ্ তা’আলা যে ন্যায়বিচারকে জরুরী ও বাধ্যতামূলক করে দিয়েছেন, তা মেনে চলতে ব্যবসায়ীদের বাধ্য করা।
( আরবি******************)
পণ্য মজুদকারী অভিশপ্ত
ইসলাম ক্রয়-বিক্রয় ও স্বাভাবিক প্রতিযোগিতা (natural competition)-এর পূর্ণ স্বাধীনতা দিলেও লোকেরা স্বার্থপরতার ও লোভের বশবর্তী হয়ে পরের ওপর টেক্কা দিয়ে নিজের ধন-সম্পদের পরিমাণ স্ফীত করতে থাকবে, তা কিছুতেই বরদাশত করতে প্রস্তুত নয়। খাদ্যপণ্য ও জনগণের সাধারণ ও নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ইত্যাদি সব ব্যাপারেই ইসলামের এ কঠোরতা। এ জন্যেই নবী রকীম (সা) পণ্য মজুদকরণের ব্যাপারে নানাভাবে কঠোর ও কঠিন ভাষায় নিষেধবাণী উচ্চারণ করেছেন। একটি হাদীসে তিনি বলেছেনঃ ( আরবি******************)
যে লোক চল্লিশ রাত্রি কাল খাদ্যপণ্য মজুদ করে রাখল, সে আল্লাহ্ থেকে নিঃসম্পর্ক হয়ে গেল এবং আল্লাহও নিঃসম্পর্ক হয়ে গেলেন তার থেকে। (আহমদ, হাকেম)
নবী করীম (সা) আরও বলেছেনঃ - ( আরবি******************)
অপরাধী ব্যক্তি ছাড়া কেউ পণ্য মজুদ করে রাখার কাজ করে না। (মুসলিম)
এ ‘অপরাধী’ কথাটি খুব সহজ অর্থে নয়। ‘যে-ই পণ্য মজুদ রাখার কাজ করে সে-ই অপরাধী’ কথাটি যথার্থ। কুরআন মজীদে ফিরাঊন, হামান প্রভৃতি বড় বড় কাফির ও খোদাদ্রোহীদের সম্পর্কে এ শব্দটির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। যেমন বলা হয়েছেঃ ( আরবি******************)
নিশ্চয়ই ফিরাঊন ও হামান ও সে দুজনার সৈন্য-সামন্ত বড় বড় অপরাধী ছিল।
পণ্য মজুদকারীর মনস্তত্ত্ব ও বীভৎস মনোভাবের ব্যাখ্যা দিয়ে নবী করীম (সা) বলেছেনঃ ( আরবি******************)
পণ্য মজুদকারী ব্যক্তি অত্যন্ত খারাপ লোক হয়ে থাকে। সে যদি শুনতে পায় যে, পণ্যমূল্য কমে গেছে, তাহলে তার খুব খারাপ লাগে। আর যদি শুনতে পায় যে, মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে তা হলে খুবই উল্লসিত হয়ে উঠে। (রাজিন)
তিনি আরও বলেছেনঃ ( আরবি******************)
বাজারে পণ্য আমদানীকারক রিযক প্রাপ্ত হয়। আর পণ্য মজুদকারী হয়ে অভিশপ্ত।
তার কারণ হচ্ছে ব্যবসায়ীর মুনাফা লাভ দুইটির কোন একটি কারণে সম্ভবপর হয়। একটি হচ্ছে, সে পণ্যদ্রব্য মজুদ করে রাখবে অধিক মূল্যে বিক্রয় করার আশায় অর্থাৎ পণ্য আটক করে রাখলে বাজারে তার অভাব তীব্র হয়ে দেখা দেবে এবং লোকেরা খুবই ঠেকায় পড়ে যাবে। তখন তার যে মূল্যই দাবি করা হবে তা যত বেশি ও সীমালংঘনকারীই হোক না কেন। তাই দিয়েই লোকেরা তা ক্রয় করতে বাধ্য হবে।
আর দ্বিতীয় হচ্ছে, ব্যবসায়ী পণ্য বাজারে নিয়ে আসবে এবং অল্প স্বল্প মুনাফা নিয়েই তা বিক্রয় করে দেবে। পরে এ মূলধন দিয়ে সে আরও অন্যান্য পণ্য নিয়ে আসবে। তাতেও সে মুনাফা পাবে। এ ভাবে তার ব্যবসা চলতে থাকতে ও পণ্যদ্রব্য বেশি কাটতি ও বিক্রয় হওয়ার ফলে অল্প অল্প করে মুনাফা করতে থাকবে। মুনাফা লাভের এই নীতি ও পদ্ধতিই সমাজ সমষ্টির পক্ষে কল্যাণকর। এতে বরকত বাড়ে। আর নবী করীম (সা) যেমন বলেছেন, এই ব্যবসায়ীই রিযিক প্রাপ্ত হয়।
পণ্য মজুদকরণ ও পণ্যদ্রব্য নিয়ে খেলা করা যে কত বড় অপরাধ, তা রাসূলে করীমের অপর একটি বাণী থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠে। হযরত মাকার ইবনে ইয়ামার (রা) বর্ণনা করেছেন, তিনি যখন রোগাক্রান্ত হলেন তখন উমাইয়া প্রশাসক উবায়দুল্লাহ ইবনে জিয়াদ তাঁকে দেখতে এলেন। তাঁকে সম্বধন করে বললেন, হে মাকাল, আপনি কি জানেন, আমি কোন হারাম রক্তপাত করেছি? বললেন, আমি জানি না। জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি জানেন আমি মুসলমানদের পণ্যদ্রব্যের মধ্যে কোন হস্তক্ষেপ করেছি? বললেনঃ তাও আমি জানি না। পরে মাকাল লোকদের বললেনঃ আমাকে বসিয়ে দাও। লোকেরা তাঁকে বসেয়ে দিলেন এবং বললেনঃ হে উবায়দুল্লাহ! শুনুন, আমি একটি হাদীস আপনাকে শোনাচ্ছি, যা রাসূলে করীমের কাছ থেকে আমি মাত্র এক-দুইবার শুনিনি। তিনি বলেছেনঃ ( আরবি******************)
মুসলিম জনগণের জন্যে পণ্যদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্য যদি কেউ কোনরূপ হস্তক্ষেপ করে, তাহলে আল্লাহ্ তা’আলার অধিকার রয়েছে তিনি কিয়ামতের দিন তাকে আগুনের ওপর বসাবেন। (আহমদ, তাবারানী)
একথা শুনে উমাইয়া শাসক বললেনঃ আপনি কি নিজেই এই হাদীস রাসূলে করীম (সা)-এর মুখে শুনেছেন? বললেনঃ হ্যাঁ, এক-দুইবার নয়।
এসব হাদীস ও তার ইঙ্গিত-ইশারার ভিত্তিতে আলিমগণ এ মাসলা বের করেছেন যে, পণ্য মজুদকরণ দুটি শর্তে হারাম। একটি এইঃ
এমন এক স্থানে ও এমন সময় পণ্য মজুদ করা হবে যখন তার কারণে জনগণকে খুবই অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে।
আর দ্বিতীয় হচ্ছে, তার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হবে অধিক মূল্য হরণ, যার ফলে মুনাফার পরিমাণ অনেক বেড়ে যাবে।
বাজারের স্বাধীনতায় কৃত্রিম হস্তক্ষেপ
পণ্য মজুদকরণের মতো আরও একটি কাজ করতে নবী করীম (সা) নিষেধ করেছেন। আর তা হচ্ছে, শহরবাসীর গ্রামবাসীর কাছ থেকে মাল ক্রয় করে নেয়। তার রূপটা হচ্ছে, শহরের বাইরের লোক মাল নিয়ে শহরের বাজারে এল চলতি দামে বিক্রয় করে দেয়ার উদ্দেশ্যে। কিন্তু শহরের লোক বললঃ এ মাল আমার কাছে রেখে যাও, পরে বেশি দামে বিক্রয় করে তোমাকে মূল্য ফেরত দেব। এমতাবস্থায় গ্রাম থেকে আশা লোকই যদি নিজে মাল বিক্রয় করত তাহলে তা সস্তায় বিক্রয় হতো। তাতে সে নিজেও মুনাফা লাভ করত এবং অন্যরাও- শহরের ক্রেতারাও লাভবান হতো।
সেকালের সমাজে এরূপ ক্রয়-বিক্রয়ের খুব বেশি ও ব্যাপক প্রচলন ছিল। হযরত আনাম বলেছেনঃ ( আরবি******************)
কোন শহরবাসী যেন গ্রামবাসীর পণ্য বিক্রয় না করে- এ বিষয়ে আমাদের নিষেধ করা হয়েছে। সে লোক তার নিজের ভাই, পিতা বা মাতাই হোক-না-কেন।
এ থেকে জানা গেল ইসলামে ব্যক্তিগত সম্পর্ক ও আত্মীয়তার চাইতে সামষ্টিক কল্যাণের গুরুত্ব অনেক বেশি।
নবী করীম (সা) বলেছেনঃ ( আরবি******************)
কোন শহরের লোক যেন গ্রাম্য লোকের পণ্য বিক্রয় না করে। তোমরা লোকদের ছেড়ে দাও। আল্লাহ্ তাদের কারোর দ্বারা কাউকে রিযক দেয়ার ব্যবস্থা করবেন।
রাসূলে করীম (সা)-এর এই কথাটি গুরুত্বপূর্ণ। এ থেকে ব্যবসা পর্যায়ে একটা বড় মূলনীতি লাভ করা যাচ্ছে। তা হচ্ছে, বাজারে পণ্য ও স্বাভাবিক পন্থার বিনিময় প্রণালীকে নিজস্বভাবে কাজ করার অবাধ সুযোগ দিতে হবে। এ ব্যাপারে কোনরূপ হস্তক্ষেপ না করা হলে স্বাভাবিক পন্থায়ই লোকেরা নিজের নিজের রিযক লাভ করতে সক্ষম হবে।
উপরিউক্ত হাদীসের সঠিক তাৎপর্য কি, তা হযরত ইবনে আব্বাসের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল। জবাবে তিনি বলেছিলেনঃ ( আরবি******************)
বিক্রেতা ও ক্রেতার মাঝখানে কোন দালাল থাকবে না। (বুখারী)
তার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, কেউ যখন তাকে মূল্য জানিয়ে দিল, তাকে উপদেশ দিল এবং বাজারের অবস্থার সাথে তাকে পরিচিত করল এবং তাতে কোন মজুরী গ্রহণ না করল, তাহলে তাতে কোন দোষ নেই। কেননা তার এ উপদেশ দান একান্তভাবে আল্লাহর জন্যে। এ উপদেশ দান দ্বীনের অংশ; বরং তা-ই সম্পূর্ণ ও সমগ্র দ্বীন। সহীহ্ হাদীসে উদ্ধৃত হয়েছেঃ ( আরবি******************) দ্বীনই হচ্ছে নসীহত বা নসীহতই হচ্ছে দ্বীন।
অপর একটি হাদীসে বলা হয়েছেঃ ( আরবি******************)
তোমাদের কেউ উপদেশ চাইলে তার ভাইকে উপদেশ দেয়া তার কর্তব্য।
‘দালাল’ সাধারণতঃ তার মজুরী পাওয়ার জন্যেই লালায়িত হয়। আর এসব ব্যাপারে সে সাধারণ মানুষের কল্যাণের কথা প্রায়ই ভুলে যায়।
দালালী জায়েয
অন্যান্য কাজে দালালী করা হলে, তাতে কোন দোষ নেই। কেননা তা একপ্রকার পথ-প্রদর্শন, ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন এবং মাধ্যম হওয়ার ব্যাপার। তার দরুন উভয় পক্ষই উপকৃত হয়। উভয় পক্ষেরই নিজের নিজের কাজে অনেক অসুবিধা হয়ে যায়। বর্তমান কালে আমদানী রফতানী ব্যবসায়ে এবং খুচরা বা পাইকারী ব্যবসায়ীদের মধ্যস্থতার বড় প্রয়োজন দেখা দেয়। অতীতের যে কোন কালের বা যুগের তুলনায় একালে ও এযুগে এ প্রয়োজন তীব্রতর। আর তাতে দালালের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা অস্বীকার করার উপায় নেই।
তাই দালাল যদি তার নির্দিষ্ট মজুরী নগদ গ্রহণ করে কিংবা মুনাফা থেকে হার মতো কমিশন অথবা অন্য কোনভাবে উভয় পক্ষ সম্মত হয়ে নেয়, তবে তাতে কোন দোষ নেই। ইমাম বুখারী লিখেছেন- ইবনে সিরীন, আতা, ইবরাহীম, হাসান প্রমুখ প্রখ্যাত ফিকাহবিদ দালালীর মজুরী গ্রহণে কোন দোষ দেখতে পান নি। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেনঃ যদি একজন অপর জনকে বলে, ‘এ কাপড়টা বিক্রয় করে দাও। অতিরিক্ত যা পাওয়া যাবে তা তোমার’ তবে তা সম্পূর্ণ জায়েয। ইবনে সিরীন বলেছেনঃ এ জিনিসটি এ দামে বিক্রয় কর। আর বেশি যা পাবে, তা তোমার হবে কিংবা তা তুমি-আমি ভাগাভাগি করে নেব এবং এ ভিত্তিতে যদি তা বিক্রয় করে দেয়ার কাজ করা হয় তবে তাতে কোন দোষ নেই। এ দালালী ব্যবসা কমিশন এজেন্সী ধরনের কাজ সম্পূর্ণ জায়েয। নবী করীম (সা) বলেছেনঃ ( আরবি******************)
মুসলমান নিজেদের পারস্পরিক শর্ত মেনে চলতে বাধ্য। (বুখারী)
মুনাফাখোরি ও ধোঁকাবাজি হারাম
বাজার বা স্বাভাবিক দ্রব্যমূল্যের ওপর কৃত্রিমভাবে হস্তক্ষেপ করতে নিষেধ করার সাথে সাথে নবী করীম (সা) মুনাফাখোরি ও ধোঁকাবাজি করতেও স্পষ্ট ভাষায় নিষেধ করেছেন। হাদীসে এ কথাটি বোঝার জন্যে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। হযরত ইবনে উমর (রা) এর ব্যাখ্যায় বলেছেনঃ পণ্যের ন্যায্য মূল্যের অধিক বুলি দেয়া অথচ তুমি তা কিনবার ইচ্ছা পোষণ কর না। আর তুমি তা কর এ জন্যে যে, তোমার বুলি শুনে অন্য লোকেরা তোমার অনুসরণ করবে। সাধারণত অন্যদের ধোঁকা দেয়ার উদ্দেশ্যেই এরূপ করা হয়।
বেচা-কেনা কারবারটিকে মুনাফাখোরি থেকে এবং দ্রব্যমূল্যকে ধোঁকাবাজি থেকে মুক্ত ও পবিত্র রাখার উদ্দেশ্যে নবী করীম (সা) বাজারে মাল আসার পূর্বেই- বাইরে-বাইরে- ক্রয় করতে নিষেধ করেছেন নতুবা মূল বাজারেই পণ্যদ্রব্যের আমদানী ব্যাহত হয়ে পড়বে। আর তার ফলে সঠিক মূল্যও নির্ধারিত হতে পারবে না। কেননা সঠিক মূল্য নির্ধারণ বাজারে পণ্যের আমদানী ও তার চাহিদা (demand) অনুপাত সম্ভবপর হয়। কিন্তু উপরিউক্ত অবস্থায় বিক্রেতা বাজারের দর-দাম কিছু জানতে পারে না। এ কারণেই নবী করীম (সা) বাজারে পণ্য পৌঁছার পর পূর্ববর্তী সওদা ভঙ্গ করার অধিকার বিক্রেতার আছে বলে ঘোষণা করেছেন। ( আরবি******************)
যে ধোঁকাবাজি করল সে আমাদের নয়
ইসলাম ধোঁকা-প্রতারণার সবল রূপ ও পন্থাকে হারাম করে দিয়েছে। তা ক্রয় বিক্রয় সম্পর্কেই হোক কিংবা অন্যান্য মানবীয় ব্যাপারেই মুসলমান সততা ও ন্যায়পরতা অবলম্বন করবে। ইসলামের দৃষ্টিতে সর্বপ্রকার বৈষয়িক কামাই-রোযগারের তুলনায় ‘দ্বীনের মধ্যে নসীহত’ অত্যধিক মুল্যবান ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ।
নবী করীম (সা) বলেছেনঃ ( আরবি******************)
ক্রেতা-বিক্রেতার কথাবার্তা যতক্ষণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে না। ততক্ষণে তাদের (চুক্তি ভঙ্গ করার) ইখতিয়ার থাকবে। যদি তারা দুজনই সততা অবলম্বন করে ও পণ্যের দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করে, তাহলে তাদের দুজনের এই ক্রয়-বিক্রয়ে বরকত হবে। আর যদি তারা দুজন মিথ্যার আশ্রয় নেয় ও দোষ গোপন করে, তাহলে তাদের এই ক্রয়-বিক্রয়ের বরকত নির্মূল হয়ে যাবে। (বুখারী)
তিনি আরও বলেছেনঃ ( আরবি******************)
কোন পণ্য বিক্রয়ে পণ্যের দোষ-ত্রুটি বলে দেয়া না হলে হালাল হবে না কারো জন্যেই। আর যে তা জানে, কিন্তু জানা সত্ত্বেও যদি না বলে তবু তা তার জন্যে হালাল নয়। (হাকেম, বায়হাকী)
রাসূলে করীম (সা) বাজারে গিয়ে দেখলেন, এক ব্যক্তি শস্য বিক্রয় করছে। তা তাঁর খুব পছন্দ হলো। পরে তিনি স্তুপের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিলেন। দেখলেন হাত ভিজে গেল। তখন তিনি বিক্রেতাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ ‘হে শস্য ব্যবসায়ী, এসব কি,? সে বললঃ ‘বৃষ্টির পানিতে ভিজে গেছে।, তখন নবী করীম (সা) বললেনঃ ( আরবি******************)
তাহলে তুমি এ ভিজা শস্যগুলো স্তুপের উপরিভাগে রাখলে না কেন, তাহলে ক্রেতারা তা দেখতে পেত?... এ তো ধোঁকা। আর যে আমাদের সাথে ধোঁকাবাজি করবে সে আমাদের দলভুক্ত নয়। (মুসলিম)
অপর এক বর্ণনায় বলা হয়েছেঃ নবী করীম (সা) অপর এক খাদ্য বিক্রেতার কাছে গেলেন। সে খুব ভাল পণ্য নিয়ে বসেছিল। তিনি তার ভিতরে হাত ঢুকিয়ে দিলেন। দেখলেন খুব নিকৃষ্ট মানের খাদ্য নীচে রয়েছে। তখন তিনি তাকে বললেনঃ ( আরবি******************)
এ খাবার আলাদা বিক্রয় করবে এবং এ খাবার স্বতন্ত্রভাবে বিক্রয় করবে। জেনে রাখ, যে আমাদের সাথে ধোঁকাবাজি করবে, সে আমাদের মধ্যের কেউ নয়। (আহমদ)
আগের কালের মুসলমানরা এ নীতি অনুসরণ করে চলতেন। পণ্যদ্রব্যে যে দোষত্রুটি থাকত, তা স্পষ্ট ভাষায় বলে দিতেন। তার কিছুই গোপন করতেন না। আর ক্রয় বিক্রয়ে সদা সত্য কথা বলতেন, মিথ্যার প্রশ্রয় দিতেন না। তাঁরা লোকদের কল্যাণ চাইতেন, কাউকে ধোঁকা দিতেন না।
প্রখ্যাত ফিকাহবিদ ইবনে সিরীন একটি ছাগী বিক্রয় করলেন। ক্রেতাকে তিনি বললেন, ছাগীটির দোষ আছে তা তোমাকে বলে আমি দায়িত্ব মুক্ত হতে চাই। ওটি ঘাস পা দিয়ে এদিক-ওদিক ছড়িয়ে দেয়।
হাসান ইবনে সালেহ একটি ক্রীতদাসী বিক্রয় করলেন। ক্রেতাকে বললেন, মেয়েটি একবার থুথুর সাথে রক্ত ফেলেছিল। তা ছিল মাত্র একবারের ঘটনা। কিন্তুতা সত্ত্বেও তাঁর ঈমানদার অন্তর তার উল্লেখ না করে চুপ থাকতে পারল না, যদিও তাতে মূল্য কম হওয়ার আশংকা ছিল।
বারবার কিরা-কসম করা
ধোঁকাবাজির সাথে মিথ্যামিথ্যি কিরা-কসম করা হলে এ কাজ অধিক মাত্রায় হারাম হয়ে দাঁড়ায়। নবী করীম (সা) ব্যবসায়ীদের কিরা-কসম করতে সাধারণভাবে এবং বিশেষভাবে মিথ্যা কিরা-কসম করতে স্পষ্ট ভাষায় নিষেধ করেছেন। বলেছেনঃ ( আরবি******************)
কিরা-কসম দ্বারা পণ্য তো বিক্রয় করা যায়; কিন্ত বরকত পাওয়া যায় না।
বিক্রয়ে বেশি বেশি কিরা-কসম করা নবী করীমের আদৌ পছন্দ নয়। কেননা তাতে প্রথমতঃ চুক্তির পক্ষদ্বয়ের ধোঁকাবাজির মধ্যে পড়ে যাওয়ার আশংকা রয়েছে। আর দ্বিতীয়তঃ তাতে আল্লাহর পবিত্র নামের ইজ্জত নষ্ট হওয়ারও ভয় আছে।
মাপে-ওজনে কম করা
পণ্য বিক্রয়ে পাত্র দ্বারা মাপায় বা পাল্লা দ্বারা ওজন করে কম দেয়াও এক প্রকারের ধোঁকাবাজি। কুরআন মজীদে এ ব্যাপারটির ওপর খুব বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে এবং সূরা আল-আন’আম-এর শেষে দশটি উপদেশের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আয়াতটি এইঃ ( আরবি******************)
তোমরা মাপার পাত্র ও ওজনের পাল্লা সুবিচার সহকারে পূর্ণ ভর্তি করে দাও। মানুষের সাধ্য-সামর্থ্যের অধিক আমরা কোন দায়িত্বই তার ওপর চাপিয়ে দিই না।
বলেছেনঃ ( আরবি******************)
আর তোমরা মাপার কাজ যখন করবে তখন পূর্ণ করে মাপবে। আর সুদৃঢ়-সঠিক দাঁড়ি-পাল্লার দ্বারা ওজন করবে। এ নীতি অতীব কল্যাণকর এবং পরিণতির দিক দিয়ে খুবই ভাল ও উত্তম। (সূরা বনী-ইসরাঈলঃ ৩৫)
বলেছেনঃ ( আরবি******************)
মাপে ওজনে যারা কম করে তাদের জন্যে বড়ই দুঃখ। তারা যখন লোকদের কাছ থেকে কিছু মেপে নেয়, তখন পুরোপুরি গ্রহণ করে। আর যখন তাদের মেপে বা ওজন জরে দেয়, তখন কম করে দেয়। তারা কি ভেবে দেখে না যে, তারা সেই কঠিন দিনে পুনরুত্থিত হবে, যেদিন সমস্ত মানুষ রাব্বুল আলামীনের সম্মুখে দাঁড়িয়ে যাবে। (সূরা মুত্বাফফিফীনঃ১-৬)
মুসলিম মাত্রেরই কর্তব্য এ ক্ষেত্রে সাধ্যমত পূর্ণ সুবিচার নীতি ও ন্যায়পরতা অবলম্বন করা। কেননা পুরামাত্রার ও প্রকৃত সুবিচার ন্যায়পরতা হয়ত কল্পনা করা কঠিন। এ কারণেই পূর্ণমাত্রায় পরিমাপ করার নির্দেশ দেয়ার সাথে সাথে কুরআন বলেছেঃ আমরা মানুষের সাধ্যের অতিরিক্ত কোন কাজের দায়িত্ব কারো ওপর অর্পণ করি না।
যে সব জাতি তাদের পারস্পরিক কার্যাদি ও লেন-দেনে জুলুম করেছে, বিশেষভাবে পরিমাপে ও ওজনে সুবিচারনীতি লংঘন করেছে এবং লোকদের পণ্য বিক্রয়ে তাদের ঠকিয়েছে, তাদের কিসসা কুরআন মজীদে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা’আলা এসব জাতির কাছে নবী রাসূল পাঠিয়েছেন, তাঁরা তাদেরকে সংশোধন করতে ও সুবিচার নীতির দিক নিয়ে যেতে চেষ্টা করেছেন, যেমন চেষ্টা করেছেন তাদের তওহীদে বিশ্বাসী বানাবার জন্যে।
এদের মধ্যে শুয়াইব নবীর লোকদের কথাও বলা হয়েছে। তিনি তাদের উচ্চস্বরে দাওয়াত দিয়েছেন, নাফরমানীর পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। তিনি তাদের লক্ষ্য করে বলেছেনঃ ( আরবি******************)
তোমরা পরিমাণ পূর্ণ কর এবং লোকদের পক্ষে ক্ষতিকারক হয়ো না তোমরা। আর সুদৃঢ় পাল্লায় ওজন কর ও লোকদের দ্রব্যাদি কম দিও না এবং পৃথিবীতে সীমালংঘন করে বিপর্যয়কারী হইও না। (সূরা শূআরাঃ ১৮১-১৮৩)
মুসলিম সমাজের জন্যে এ নির্দেশ অবশ্য পালনীয়। তাদের জীবনে লোকদের সাথে সম্পর্কে ও সমস্ত পারস্পরিক কাজকর্মে এ নীতিই তাদের পালন করতে হবে। অতএব দুই রকমের পরিমাণ ও দুই ধরনের পাল্লায় ওজন করে বেচা-কেনা করা তাদের জন্যে জায়েয নয়। একটা নিজের জন্যে মানদণ্ড আর একটা অন্যান্য লোকদের জন্যে সাধারণ মানদণ্ড, তার নিজের জন্যে ও তার প্রিয়জনদের জন্যে এক রকমের আচরণ এবং অন্যান্য সাধারণ মানষের জন্যে ভিন্ন রকমের মানদণ্ড ইসলামে সম্পূর্ণ অচল। কেননা এরূপ হলে সে নিজের ও নিজের অনুসারীদের প্রাপ্য পুরামাত্রায় আদায় করবে, বেশিও নিয়ে বসবে। আর অপর লোকদের জন্যে কম দেবে এবং তাদের ক্ষতিগ্রস্ত করবে। কিন্তু এর মতো অবিচার আর কিছু হতে পারে না।
চোরা মাল ক্রয়
ইসলাম অপরাধ ও অপরাধ প্রবণতার বিরুদ্ধে লড়াই ঘোষণা করেছে। অপরাধীদের সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে পরিবেষ্টিত করে দিয়েছে। তাই যে মাল অপহৃত বা চুরি করে আনা হয়েছে কিংবা মালিকের কাছ থেকে অন্যায়ভাবে নিয়ে নেয়া হয়েছে তা শুনে ক্রয় করা মুসলমানের জন্যে জায়েয নয়, কেননা তা করা হলে অপহরণকারী, চোর ও ছিনতাইকারীকে তার কাজে সাহায্য করা হবে। নবী করীম (সা) বলেছেনঃ ( আরবি******************)
যে ব্যক্তি জেনে-শুনে চুরির মাল ক্রয় করল, সে তার গুনাহ্ ও অন্যায় কাজে শরীক হয়ে গেল। (বায়হাকী)
চুরি করা মালের যদি দীর্ঘদিনও অতিবাহিত হয়, তাহলেও তার গুণাহ্ দূর হয়ে যায় না। কেননা ইসলামে সময়ের দীর্ঘতা হারামকে হালাল করে দেয় না। প্রকৃত মালিকের হক নাকচ করে না। মানব রচিত আইনেও এ নীতিই অবলম্বিত হয়েছে।
সুদ হারাম
ব্যবসায়ের মাধ্যমে মুলধনের মুনাফা লাভ ইসলামে সম্পূর্ণ জায়েয। আল্লাহ্ তা’আলা ইরশাদ করেছেনঃ ( আরবি******************)
হে ঈমানদার লোকেরা! তোমারা পরস্পরের মাল অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করে না। তবে তোমাদের সংশ্লিষ্ট সকলের সম্মতিতে ব্যবসায় হলে দোষ নেই।
যারা দুনিয়ায় ব্যবসায় লিপ্ত হয় এবং দুনিয়ায় দেশ-বিদেশে সফর করে, তাদের প্রশংসা করে কুরআনে বলা হয়েছেঃ ( আরবি******************)
আর অন্যান্য যারা পৃথিবীতে চলাফেরা করে ও আল্লাহর অনুগ্রহের সন্ধান করে বেড়ায়। (সূরা মুজাম্মিলঃ ২০)
কিন্তু সুদের পন্থায় ‘মুনাফা’ লাভ করার সবল পথকে ইসলাম সম্পূর্ণরূপে বন্ধ ও হারাম করে দিয়েছে। তার পরিমাণ কম হোক, কি বেশি, ইসলামে তা সবই নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে।
তার পরিমাণ কম হোক বেশি হোক- সবই হারাম। ইয়াহূদীদের এ সুদী কারবার করতে নিষেধ করা হয়েছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা তা করেছে। এজন্যে তাদের ওপর ভর্ৎসনা করা হয়েছে। কুরআনের সর্বশেষ নাযিল হওয়া আয়াত সমূহের মধ্যে এ আয়াত একটিঃ ( আরবি******************)
হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা ভয় কর আল্লাহকে এবং সুদের অবশিষ্টাংশ পরিহার কর যদি তোমরা ঈমানদার হও। আর তা যদি না-ই কর, তাহলে আল্লাহ ও তার রাসূলের সাথে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হও। আর তোমরা যদি তওবা কর, তাহলে তোমাদের মূলধন তোমরা ফেরত পেতে পার। তোমরা জুলুমও করবে না, তোমরা মজলুমও হবে না। (সূরা বাকারাঃ ২৭৮-২৭৯)
রাসূলে করীম (সা) সুদ ও সুদখোর, সুদী কারবারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। এ সুদের ফলে সমাজ জীবনের ওপর যে বিপদ ঘনীভূত হয়ে আসে, সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দিয়েছেন। বলেছেনঃ ( আরবি******************)
সুদ ও ব্যভিচার যখন কোন দেশে-শহরে ব্যাপক হয়ে দাঁড়ায়, তখন তাদের ওপর আল্লাহর আযাব আসা অনিবার্য হয়ে পড়ে। (হাকাম)
আসমানী ধর্মসমূহের মধ্যে ইসলামে এটা কোন একক ঘোষণা নয়। ইয়াহূদীদের ধর্মগ্রন্থে পুরান নিয়ম-এ বলা হয়েছেঃ
তুমি যদি আমার প্রজাদের মধ্যে তোমার স্বজাতীয় কোন দীন-দুখীকে টাকা ধার দাও, তবে তাহার কাছে সুদ গ্রাহীর ন্যায় হইও না, তোমরা তাহার উপরে সুদ চাপাইবে না। (যাত্রা পুস্তক-২২ অধ্যায়, ২৫ স্তোত্র)
আর খ্রিস্টানদের ধর্মগ্রন্থে বলা হয়েছেঃ
তোমরা আপন আপন শত্রুদিগকে প্রেম করিও, তাহাদের ভাল করিও এবং কখনও নিরাশ না হইয়া ধার দিও, তাহা করিলে তোমাদের মহা পুরস্কার হইবে। (নূতন নিয়ম-লুক, ৩৫ স্তোত্র, ৬ অধ্যায়)
বড়ই দুঃখের বিষয় ‘পুরাতন নিয়ম’ গ্রন্থে পরিবর্তন করে সুদে টাকা না দেয়ার কথাকে কেবল ইয়াহূদী লোকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে। ‘ভাই’ বলতে কেবল তাদেরই মনে করা হয়েছে এবং অপর লোকদের জন্যে সুদের ভিত্তিতে টাকা দেয়ার কারবার চালাবার অবাধ সুযোগ করে দেয়া হয়েছে।
সুদ হারামকরণের যৌক্তিকতা
ইসলাম সুদের ব্যাপারে খুবই কঠোরতা অবলম্বন করেছে এবং তাগিদী ভাষায় হারাম করে দিয়েছে। এতে করে সামগ্রিকভাবে মানুষের কল্যাণ সাধন করেছে। তাদের নৈতিকতা, সমাজ ও অর্থনীতেকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার ব্যবস্থা করেছে।
সুদ হারাম হওয়ার যৌক্তিকতা দেখান প্রসঙ্গে আলিমগণ কয়েকটি গুরুতর কারণের উল্লেখ করেছেন, আধুনিক বিশ্লেষণ ও চিন্তা-ভাবনার ফরে তা প্রকট হয়ে উঠেছে।
ইমাম রাযী তাঁর তাফসীরে এ পর্যায়ে যা লিখেছেন, তার উল্লেখকেই আমরা যথেষ্ট মনে করছি। তিনি লিখেছেনঃ
প্রথম কথা এই যে, সুদ লোকদের কাছ থেকে অর্থ আদায় করে কোনরূপ বিনিময় ব্যতিরেকেই। কেননা যে লোক একটি টাকা দুই টাকায় বিক্রয় করে, সে একটি টাকা অতিরিক্ত গ্রহণ করে; কিন্তু সেজন্যে তাকে কিছুই দিতে হয় না। আর মানুষের টাকা তো তাদের প্রয়োজন পুরণার্থেই লাগে। তার একটি বিশেষ ও বিরাট মর্যাদাও রয়েছে। হাদীস শরীফে বলা হয়েছেঃ ( আরবি******************)
মানুষের রক্তের যে মর্যাদা, মানুষের ধন-মালেরও ঠিক সেই মর্যাদা।
এ কারণে কোনরূপ বিনিময় না দিয়ে তা গ্রহণ করা সম্পূর্ণ হারাম হওয়াই বাঞ্ছনীয়।
দ্বিতীয়তঃ সুদের মাধ্যমে অর্থাগমের ওপর নির্ভরশীলতা মানুষকে শ্রম করে উপার্জন করা থেকে বিমুখ ও অনুৎসাহী বানিয়ে দেয়। সুদী করবার বা সুদ ভিত্তিক লগ্নির ফলে যখন অতিরিক্ত অর্থ পাওয়াই যাচ্ছে, তা নগদ হোক বা বাকী, তখন শ্রম করে, ব্যবসায় ও শিল্পোৎপাদনের খাটাখাটুনির কোন প্রয়োজন বোধই লোকদের মধ্যে জাগবে না এবং তার দরুন সামষ্টিক কল্যাণ ব্যবস্থা ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাবে। আর ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প-কৃষি ও নির্মাণ প্রভৃতি কার্য সম্পন্ন না হলে মানব-সাধারণের কোন কল্যাণের চিন্তা বা আশাই করা যায় না।
আমাদের মতে অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ দিয়ে সুদ হারাম হওয়ার এ-ই হচ্ছে কারণ।
তৃতীয় কথা, সমাজের লোকদের মধ্যে প্রচলিত নিয়মে ঋণ দেয়া-নেয়ার ব্যবস্থা এর দরুন ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়। কেননা সুদ যখন হারাম গণ্য করা হবে, তখন মানুষের মন এজন্যে প্রস্তুত হবে যে, তারা এক টাকা ঋণ বাবদ গ্রহণ করলে সেই এক টাকাই ফেরত দেবে। কিন্তু সুদ যদি হালাল বা প্রচলিত হয়, তাহলে প্রয়োজন মানুষকে এক টাকার পরিবর্তে দুই টাকা দিতে ও গ্রহণ করতে বাধ্য করবে। তার ফলে লোকদের পারস্পরিক সহৃদয়তা, কল্যাণ কামনা ও দয়া অনুগ্রহ বলতে কোন জিনিসের অস্তিত্বই থাকবে না।
আর এ হচ্ছে সুদ হারাম হওয়ার নৈতিক কারণ।
চতুর্থ, সাধারণত ঋণদাতা ধনী এবং ঋণগ্রহীতা দরিদ্র ব্যক্তি হয়ে থাকে। এক্ষণে সুদ-ভিত্তিক ঋণ-দান ব্যবস্থা চালু থাকলে ধনী ব্যক্তিকে গরীব দুর্বল ব্যক্তির কাছ থেকে অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণের অধিকারী বানিয়ে দেয়া হবে। কিন্ত মহান দয়াময় আল্লাহর অনুগ্রহমূলক ব্যবস্থায় তা কিছুতেই জায়েয হতে পারে না।
এ হচ্ছে সামাজিক দৃষ্টিতে সুদ হারাম হওয়ার কারণ এবং তার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, সুদ ব্যবস্থায় শক্তিমানের স্বার্থে দুর্বলকে শোষণ করার অবাধ সুযোগ ঘটে। তার ফলে ধনী আরও ধনী হয়ে যায় এবং গরীব আরও গরীবীর মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয় এবং সমাজের এক শ্রেণীর লোক দিন দিন মোটা হয়ে উঠে অন্যান্য বহু কয়টি শ্রেণীর লোককে পেশাষণ করে, শেষ করে। আর তার ফলে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকদের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ তীব্র হতেও তীব্রতর হয়ে উঠে। সমাজের মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও সংগ্রামের আগুন জ্বালাতে থাকে দাঊ দাঊ করে। শেষ পর্যন্ত তার পরিণতি দেখা দেয় চরম ধ্বংস ও সামষ্টিক বিপর্যয়। আধুনিক কালের সমাজ ইতিহাস থেকেও এ কথার সত্যতা ও যথার্থতা প্রমাণিত। দেখা যায়, এ সুদ ও সুদখোর লোকেরাই রাজনীতির, রাষ্ট্র, প্রশাসন ও শান্তি নিরাপত্তার পক্ষে বিরাট হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে।
সুদদাতা ও সুদী দলিলের লেখক
ধনী লোকেরাই সুদ খায় ও সুদের ভিত্তিতে ঋণ দেয়। সে ঋণী ব্যক্তিকে টাকা দেয়া, যেন মূলধনের ওপর সে বাড়তি টাকা ফেরত দেয়। এরূপ ব্যক্তি আল্লাহর কাছেও যেমন অভিশপ্ত হয়ে থাকে, তেমনি জনগণের কাছেও। কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিতে কেবল সুদখোররাই অপরাধী হয় না, যারা সুদ দেয়, সুদ খাওয়ায়, তারাও এই অপরাধে শরীক রয়েছে। সুদের দলিল যারা লেখে এবং তাতে যারা সাক্ষী হয়, তারাও কোন অংশে কম অপরাধী নয়। হাদীসে বলা হয়েছেঃ ( আরবি******************)
যে সুদ খায়, সুদ খাওয়ায়, তার সাক্ষী হয় এবং তার দলিল লেখে, তাদের সকলেরই ওপর আল্লাহ্ তা’আলা অভিশাপ করেছেন। (মুসনাদে আহমদ, আবূদাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ)
অবশ্য সুদের ভিত্তিতে ঋণ গ্রহণ করার যদি তীব্র প্রয়োজন দেখা দেয়, তাহলে শুধু সুদখোরই গুনাহগার হবে। তবেঃ
১. যদি বাস্তবিকই তার প্রয়োজন থাকে। নিছক নিজের প্রয়োজন পূরণ বা উন্নয়নমূলক কাজের ব্যাপকতা বিধান তার লক্ষ্য হবে না। প্রয়োজনের অর্থ, মানুষ তা থেকে বাঁচতে চেয়েও বাঁচতে পারে না, নিজেকে ধ্বংস করতে প্রস্তুত হওয়া ছাড়া। যেমন খাদ্য, কাপড়, চিকিৎসা প্রভৃতি অপরিহার্য প্রয়োজন পূরণের জন্যে এ সুদভিত্তিক ঋণ গ্রহণ করতে মানুষ বাধ্য হয়ে পড়ে অনেক সময়।
২. কেবলমাত্র নিজের প্রয়োজন পূরণ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ হবে। যথা দশ টাকার প্রয়োজন হলে সেখানে এগারো টাকা গ্রহণ করা হবে না।
৩. সুদ থেকে মুক্তি লাভের জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা চালাতে হবে। এমন ঠেকায় পড়া ব্যক্তির সাহায্য করা মুসলিম জনগণের কর্তব্য। কিন্তু ঠেকায় পড়া ব্যক্তি যদি সুদের ভিত্তিতে ঋণ গ্রহণ করা ছাড়া আর কোন উপায়ই না পায়, তাহলে সে সুদ ভিত্তিক ঋণ গ্রহণ করতে পারে, তবে শর্ত হচ্ছে তার জন্যে তার মনে কামনা-বাসনা জাগতে পারবে না, সে ব্যাপারে সীমাও লংঘন করা চলবে না। এরূপ অবস্থা হলে হয়ত আল্লাহ্ তাকে মাপ করে দেবেন।
৪. আর ঠেকায় পড়ে এ কাজ করতে হলে অত্যন্ত ঘৃণা সহকারে এ কাজ করবে। তাতে সে সন্তুষ্ট থাকবে না, অসন্তোষ প্রকাশ করবে। যতদিন না আল্লাহ্ তার জন্যে অন্য কোন ব্যবস্থা করে দেন, শুধু ততদিনই এ কাজ করা যাবে।
ঋণ লওয়া থেকে নবী পানা চাইতেন
মুসলমান মাত্রেই একথা জানা উচিত যে, ইসলাম জীবনে ভারসাম্য সৃষ্টি ও অর্থনীতিতে মধ্যম পন্থা অনুসরণ করার হেদায়েত দিয়েছে। আল্লাহ্ তা’আলা বলেছেনঃ ( আরবি******************)
তোমরা সীমালংঘন করো না। কেননা আল্লাহ্ সীমালংঘনকারীদের পছন্দ করেন না।
( আরবি******************) বেহুদা খরচ করো না। কেননা বেহুদা অর্থ ব্যয়কারী লোকেরা শয়তানের ভাই ও দোসর হয়ে থাকে। (সূরা বনী-ইসরাঈলঃ ২৬-২৭)
কুরআন মজীদ মুসলমানদের আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় করার নির্দেশ দিয়েছে। কিন্তু আল্লাহর দেয়া সম্পূর্ণ ধন-সম্পদই ব্যয় করে দিতে বলেনি, তা থেকে তার অংশ ব্যয় করার কথাই বলেছে। আর যে লোক নিজ উপার্জন থেকে কিছু অংশ আল্লাহর পথে ব্যয় করে, সে সম্ভবত কখনই দরিদ্র ও অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়বে না। এ মধ্যম ও ভারসাম্যপূর্ণ নীতি অবলম্বনের অনিবার্য দাবি এই যে, কোন মুসলমান ঋণ প্রহণ করতে কখনই বাধ্য হবে না। বিশেষ করে নবী করীম (সা) মুসলমানের ঋণ গ্রহণ করাকে কখনই পছন্দ করেন নি। কেননা স্বাধীন মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তির জন্যে ঋণ রাতের দুশ্চিন্তা ও দিনের বেলার লাঞ্ছনার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। নবী করীম (সা) সব সময় এ ঋণ গ্রহণ থেকে আল্লাহর কাছে পানা চেয়েছেন। তিনি এই দো’আ করতেনঃ ( আরবি******************)
হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই ঋণের বোঝা বৃদ্ধি ও রুদ্র রোষ থেকে।
বলতেনঃ ( আরবি******************)
আমি কুফরি ও ঋণ থেকে আল্লাহর কাছে পানা চাই।
এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলঃ হে রাসূল! আপনার মতে কুফরি ও ঋণ কি সমান ব্যাপার? উত্তরে তিনি বললেনঃ হ্যাঁ।
তিনি নামাযে প্রায়ই দো’আ পড়তেনঃ ( আরবি******************)
হে আল্লাহ্, আমি তোমার কাছে গুনাহ ও ঋণ থেকে পানা চাই।
এক সময় তাঁকে প্রশ্ন করা হলোঃ ( আরবি******************)
হে রাসূল! আপনি ঋণগ্রস্ততা থেকে খুব বেশি বেশি পানা চান কেন? উত্তরে তিনি বললেনঃ মানুষ যখন ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ে তখন সে কথা বলতে গিয়ে মিথ্যা বলে এবং ওয়াদা করে তার খেলাফ করে। (নিসায়ী, হাকেম)
ঋণগ্রস্ততা নৈতিকতার দৃষ্টিতে যে কতখানি মারাত্মক তা এসব হাদীস থেকে অকাট্যভাবে প্রমাণ ও দিনের মতো ভাস্বর হয়ে উঠে।
কোন মৃতের লাশ জানাযা পড়ার জন্যে নবী করীম (সা)-এর কাছে নিয়ে আসা হলে; যদি জানতে পারতেন যে, সে ঋণগ্রস্ত হয়ে মরেছে এবং তা শোধ করার মতো কিছুই রেখে যায়নি, তখন তিনি তার জানাযা নামায পড়তেন না। জানাযা না পড়ে তিনি লোকদের এই ঋণগ্রস্ততার মারাত্মক পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করে দিতে চাইতেন মাত্র। উত্তরকালে রাসূলে করীম (সা)-এর হাতে যখন বিপুল গনীমতের মাল-সম্পদ জমা হলো, তখন তিনি তা থেকেই মৃতের ঋণ শোধ করার ব্যবস্থা করতেন। তিনি বলেছেনঃ ( আরবি******************)
শহীদের সব গুনাহই মাফ হয়ে যায়। কিন্তু ঋণ ক্ষমা হয় না। (মুসলিম)
এসব কথার আলোকে বলতে হয়, মুসলমানের কখনও ঋণ গ্রহণ করা উচিত নয়। তবে নিতান্ত ও কঠিন ধরনের ঠেকায় পড়ে গেলে অন্য কথা। আর এ অবস্থায় ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়লে তা শোধ করার মনোভাব প্রবল রাখতে হবে সব সময়। হাদীসে বলা হয়েছেঃ ( আরবি******************)
যে লোক অন্যদের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করল এবং তা আদায় করে দেয়ার মনোভাব রাখল, তার ঋণ আদায়ের ব্যবস্থা আল্লাহ্ তা’আলা করে দেবেন। আর যে লোক ঋণ গ্রহণ করে তা না দেয়ার বা নষ্ট করার মনোভাব নিয়ে, আল্লাহও তাঁকে বিনষ্ট করবেন। (বুখারী)
বস্তুত মুসলমান যখন নেহায়েত ঠেকায় না পড়ে কখনও ঋণ গ্রহণ করতে প্রস্তুত হতে পারে না, তখন তাকে সুদের ভিত্তিতে ঋণ গ্রহণ করতে কি করে বাধ্য করা যেতে পারে?
বেশি মুল্যে বাকী ক্রয়
এখানে আরও একটি কথার ব্যাখ্যা হওয়া আবশ্যক মনে হচ্ছে। নগদ দামে পণ্যদ্রব্য ক্রয় করা যেমন জায়েয, তেমনি পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে বাকী মূল্যে ক্রয় করাও নাজায়েয নয়। তবে তাতে একটা মেয়াদ নিদিষ্ট থাকতে হবে। নবী করীম (সা) নিজে ইয়াহূদীর কাছ থেকে তাঁর ঘরের লোকদের জন্যে বাকীতে খাদ্যপণ্য ক্রয় করেছেন। তবে সেজন্যে তিনি তাঁর লৌহবর্ম বন্ধক রেখেছিলেন।
কিন্তু বিক্রেতা যদি নগদ মূল্য না দেয়া ও বাকীতে ক্রয়ের দরুন পণ্য মূল্য বেশি ধার্য করে- অনেক বড় বড় ব্যবসায়ী মূল্য বাড়িয়ে দিয়ে ও কিস্তিতে আদায় করার শর্তে পণ্য বিক্রয় করে থাকে- অনেক ফিকাহবিদই মনে করেন, এ ধরনের বিক্রয় হারাম। কেননা মূল্য আদায় করণে যে বিলম্ব করা হচ্ছে, তার বিনিময়েই বেশি মূল্য ধার্য করা হচ্ছে। আর তা এক ধরনের সুদই বটে। তবে সাধারণ আলিম ও ফিকাহবিদগণ এরূপ বিক্রয়কে জায়েয মনে করেন। তারা বলেন, ক্রয়-বিক্রয় মূলত তো হালাল এবং জায়েয। তা হারাম বলার পক্ষে কোন দলিলই পাওয়া যেতে পারে না। আর এরূপ ক্রয়-বিক্রয় সবদিক দিয়ে সুদী কারবারের মতোও নয়। তাঁরা মনে করেন, অনেক কয়টি দিকের দিকের বিবেচনায় বিক্রেতা বাকী মূল্যে বিক্রয় করে বলে পণ্যের অতিরিক্ত মূল্য ধার্য করতে পারে, তার সে অধিকার রয়েছে। তবে তা অবশ্যই সাংঘাতিকভাবে বেশি মূল্য হওয়া উচিত নয়, তাতে ক্রেতার ওপর জুলুম হওয়ার মতো কোন অবস্থাও সমর্থনীয় নয়। নতুবা তাও হারাম হবে।
ইমাম শাওকানী লিখেছেনঃ বাহ্যত এরূপ ক্রয়-বিক্রয় জায়েযই হবে। কেননা এ পর্যায়ের কতগুলো সাধারণ দলিল প্রমাণ রয়েছে। আর শাফেয়ী, হানাফী ও যায়দ ইবনে আলী প্রমুখ ফকিহর মতেও তা জায়েয। ( আরবি******************)
আগে মূল্য দেয়া ও পরে পণ্য গ্রহণ
নির্দিষ্ট পরিমাণ মূল্য অগ্রিম বিক্রেতাকে দেয়া ও নির্দেষ্ট সময় অতিবাহিত হওয়ার পর তার বিনিময়ে পণ্য গ্রহণকে ইসলামী পরিভাষায় ‘সিলম’ বিক্রয় বলা হয় এবং তা জায়েয। মদীনায় এর ব্যাপক প্রচলন ছিল। কিন্তু নবী করীম (সা) এতে কতগুলো শর্ত আরোপ করেছেন, যা পালন করা হলে তাতে শরীয়তের সাথে পূর্ণ সামঞ্জস্য রক্ষা পায়।
হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেনঃ নবী করীম (সা) মদীনায় উপস্থিত হলেন, যখন তিনি দেখতে পেলেন যে, মদীনার লোকেরা মূল্য অগ্রিম দিচ্ছে যেন এক বছর বা দুই বছর পর তার বিনিময়ে ফসল লাভ করতে পারে।
তখন নবী করীম (সা) বললেনঃ ( আরবি******************)
যে লোক অগ্রিম মূল্য দিয়ে কোন কিছু কিনবার সাব্যস্ত করবে, সে যেন তার ওজন, পরিমাণ ও সময় সব কিছুই নির্দিষ্ট করে নেয়।
এভাবে পরিমাণ, ওজন ও সময় পূর্বেই নির্দিষ্ট হয়ে থাকলে পারস্পরিক ঝগড়া ও গণ্ডগোল হওয়ার আশংকা থাকে না। ধোঁকাবাজি করার অবকাশও অনেকটা কম হয়ে যায়। বিশেষ গাছের ফলের অগ্রিম সওদা করা থেকে নবী করীম (সা) এ জন্যেই নিষেধ করেছেন। কেননা তাতে ধোঁকা ও ঠকবাজির ভয় রয়েছে। অনেক সময় নৈসর্গিক বিপদে পড়ার দরুন গাছে আদৌ ফলই ধরে না। তখন তা সাংঘাতিক অবস্থা দেখা দেয়।
এ পর্যায়ের কারবারের সঠিক পন্থা এ হতে পারে যে, বিশেষ গাছ বা বিশেষ জমির ফসলের শর্ত লাগানো উচিত নয়। কেবল ওজন ও পরিমাণ নির্ধারণ করে সওদা করা যেতে পারে। কিন্তু গাছ বা জমির মালিকের কাছ থেকে যদি অবৈধভাবে স্বার্থ উদ্ধার করা হয়। অর্থাৎ সে যদি এ সওদা করতে বাধ্য হয়, তাহলে তা হারাম হওয়ার সম্ভাবনা।
শ্রম ও মূলধনের পারস্পরিক সহযোগিতা
কেউ কেউ বলেন, আল্লাহ্ তা’আলা তাঁর নিজস্ব সৃষ্টি কৌশল অনুযায়ী মানুষকে স্বীয় অফুরন্ত নিয়ামতে ধন্য করেছেন। কত মানুষই এমন, যাদের মধ্যে জ্ঞান-প্রতিভা ও কর্মক্ষমতা অসীম, কিন্তু তাদের কাছে অর্থ নেই। পক্ষান্তরে বহু লোক এমনও রয়েছে, যাদের অর্থের কোন পরিমাপ সীমা নেই, কিন্তু যোগ্যতা ও কর্মক্ষমতা থেকে বঞ্চিত। এক্ষণে প্রশ্ন উঠে, যাদের কাছে ধন-সম্পদ রয়েছে, তারা তাদের ধন-সম্পদ কর্মক্ষমতা সম্পন্ন লোকদের হাতে সঁপে দেয় না কেন? তারা তা পেলে শ্রম মেহনত করে সেই ধন-সম্পদকে অধিক কল্যাণময় রাখতে পারে। আর ধনমালের অধিকারীরা নিজেদের ধনের বিনিময়ে বিপুল মুনাফার অংশীদারও হতে পারে।
এ প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলব, ইসলামী শরীয়ত মূলধন ও কর্মক্ষমতা অথবা মূলধন ও শ্রমের মধ্যে সমন্বয় ও সহযোগিতার পথে কোন প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেনি। বরং ইনসাফ ও সুবিচারের ভিত্তিতে ও নির্ভুল সঠিক ব্যবস্থাপনার অধিন সহযোগিতার পন্থা উদ্ভাবন করেছে। অতএব ধনশালী ব্যক্তি যদি তার সঙ্গীর সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কোন মুনাফামূলক কারবার করতে চায় তাহলে এ অংশীদারিত্বের সমস্ত ফলাফলকে দায়িত্ব সহকারে তাকে তা গ্রতণ করতে হবে। ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় তাকে বলা হয় ‘মুজারিবাত’ কিংবা ‘কিরাজ’। ফিকাহবিদগণ এ কাজে শর্ত আরোপ করেছেন যে, কারবারের উভয় পক্ষকেই লাভ বা লোকসান সব কিছুতেই শরীক হতে হবে এবং তার হার নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিতে হবে। তা শতকরা পঞ্চাশ ভাগ, এক-তৃতীয়াংশ কিংবা এক-চতুর্থাংশ এক পক্ষের জন্যে হবে, আর অবশিষ্ট হবে অপর পক্ষের। মূল কারবার এভাবে ঠিক হয়ে যাওয়ার পর তাতে মুনাফা হলে চুক্তি অনুযায়ী তা পক্ষদ্বয়ের মধ্যে বন্টন হবে। আর লোকসান হলে মুনাফা থেকে তা বাদ দিয়ে নিয়ে হার মতো ভাগ করে নিতে হবে। আর মুনাফার তুলনায় লোকসান যদি বেশি হয় তাহলে এ অতিরিক্ত লোকসান মূলধন থেকে নিয়ে নেয়া হবে। মূলধনের মালিককে লোকসানের অংশ তার মূলধন থেকে কেটে দেয়া কর্তব্য, এতে আশ্চর্যের কিছুই নেই। কেননা তার অংশীদারকেও শ্রম ও মেহনতের ক্ষতিটা মেনে নিতে হচ্ছে।
সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে এ-ই ইসলামের বিধান। মূলধনের মালিকের জন্যে মুনাফার সীমা নির্ধারণ ও তার নিরাপত্তা দেয়া- সে লাভ হোক, লোকসান হোক, তাকে মুনাফা দিয়ে যাওয়াই হবে, তা সুবিচার নীতি ও ইনসাফ ব্যবস্থার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। তাতে যোগ্যতা ও শ্রমের ওপর মূলধনকে প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি ও অকারণ অগ্রাধিকার দেয়া হয়। উপরন্তু তা সেই জীবন পদ্ধতিরও বিরোধী যা মানুষের জন্যে যেমন মুনাফার ব্যবস্থা করে, তেমনি ক্ষতিকরও। শুধু তা-ই নয়, তদ্দরুন উপার্জনকে নিশ্চিতকরণের ঝোঁক-প্রবণতাকেও সমর্থন দেয়া হয়। তার জন্যে না শ্রম করার প্রয়োজন, না ক্ষতির ঝুঁকি মাথা পেতে নেয়ার কোন কারণ দেখা দেয়। ফলে তা প্রকৃতপক্ষে সুদ ও সুদী কারবারের মতোই হয়ে দাঁড়ায়।
নবী করীম (সা) এ রকম ভাগে জমি চাষ করতে দিতে নিষেধ করেছেন যে, জমির একটা নির্দিষ্ট অংশের ফসল এক পক্ষ পাবে আর অপর পক্ষ পাবে অপর নির্দিষ্ট অংশের ফসল। ফসলের একটা নির্দিষ্ট পরিমাণের ওপরও ভাগ চাষ করতে নিষেধ করেছেন। কেননা এটা ঠিক সুদ বা জুয়ার মতোই ব্যাপার। হতে পারে যে, জমির সেই নির্দিষ্ট অংশে কোন ফসলই হলো না অথবা সেই নির্দিষ্ট পরিমাণের অধিক ফসলও হলো না। তাতে এক পক্ষের সম্পূর্ণ বঞ্চিত থেকে যাওয়ার অবস্থা হতে পারে। অথচ অপর পক্ষ পূর্ণভাবে লাভবান হয়ে যাবে। আর এ অবস্থা কোনক্রমেই ইনসাফপূর্ণ হতে পারে না।
মুজারিবাত ইসলামে জায়েয। কিন্তু সেজন্যে শর্ত এই যে, মূল বারবারের লাভ-লোকসানের দিক খেয়াল না রেখে এক পক্ষের জন্যে নিশ্চিত মুনাফার ব্যবস্থা থাকতে পারবে না। এ মতের ওপর ইজমা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সে শর্ত হলে ‘মুজারিবাত’ জায়েয হবে না ঠিক যে কারণে ‘মুজারিবাত’ জায়েয হয় না। পারস্পরিক জমি চাষের ব্যাপারটিও অনুরূপ কারণে নাজায়েয হয়ে যায়। ফিকাহবিদগণ বলেন, এক পক্ষ যদি নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকাই মুনাফা লাভের শর্ত ধার্য করে, আর কারবারের ফলে অতটা পরিমাণ টাকাই মুনাফা হয়, তাহলে তার অর্থ হবে, সমস্ত মুনাফা এক পক্ষই পেয়ে গেল; বরং আদপেই মুনাফা না হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। আর যদি বেশি মুনাফা পাওয়ার শর্তে কারবার করেছে সে ক্ষতিগ্রস্ত হতে বাধ্য হবে। ( আরবি******************)
উপরের বর্ণিত কারণটি ইসলামের মৌলিক ভাবধারার সাথে পুরা মাত্রায় সঙ্গতিপূর্ণ। বস্তুত ইসলামের সকল নীতি ও বিধানই সুদৃঢ়, সুস্পষ্ট ও নিরেট ইনসাফের ওপর ভিত্তিশীল।
মূলধনের পারস্পরিক অংশীদারিত্ব
ব্যক্তিগতভাবে নিজের মূলধন নিজের ইচ্ছামত কোন মুবাহ কাজে বিনিয়োগ করা ও তা থেকে মুনাফা লাভ করা, উপরন্ত কোন অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিকে মুজারিবাতের বিধান অনুযায়ী কারবার করার জন্যে দেয়া যেমন জায়েয, অনুরূপ মূলধন বিনিয়োগকারী লোকেরা একত্র ও পারস্পরিকভাবে সম্মত হয়ে কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান, ব্যবসায়ী ফার্ম বা সংস্থা গড়ে তোলা অথবা অন্য কোন কারবারে পারস্পরিক শরীকদারীর ভিত্তিতে কাজ করাও সম্পর্ণ জায়েয। কেননা অনেক ধরনের কারবার এমন হয়ে থাকে, যার জন্যে বহু সংখ্যক হস্তের বুদ্ধিমানের ও বিরাট পরিমাণ মূলধনের একত্র সমাবেশ একান্তই অপরিহার্য। আর তা পারস্পরিক সহযোগিতা ও শরীকদারীর মাধ্যমেই পূরণ হতে পারে। আল্লাহ্ তা’আলা ইরশাদ করেছেনঃ ( আরবি******************)
তোমরা কল্যাণময় পুণ্যময় ও আল্লাহ্ ভীতির কাজে পরস্পর সহযোগিতা কর।
আর যে কাজই ব্যক্তি বা সমাজ-সমষ্টির কল্যাণ সাধন বা অকল্যাণ প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে করা হবে, তা-ই কল্যাণময় এবং আল্লাহ্ ভীতির কাজ, তাতে সন্দেহ নেই। তবে শর্ত এই যে, তা অবশ্যই ভাল নিয়্যত ও মন-মানসিকতা সহকারে সম্পন্ন করতে হবে।
পারস্পরিক শরীকদারীকে ইসলাম শুধু জায়েয ও সঙ্গত ঘোষণাই করেনি; বরং তাতেই বরকত নিহিত বলেছে। তাতে যেমন দুনিয়ায় আল্লাহর সাহায্য পাওয়ার ওয়াদা রয়েছে, তেমনি পরকালেও তাতেই বিপুল সওয়াব পাওয়ার আশা। তবে তা জায়েয সীমার মধ্যে থেকে ও সুদ, ধোঁকা,প্রতারণা, জুলুম, লোভ-লালসা ও খিয়ানতকরণ থেকে সযত্নে দূরে থেকে শরীকদারীর কারবার করতে হবে। নবী করীম (সা) এরূপ শরীক ব্যবসায়ীদের সম্পর্কেই বলেছেনঃ ( আরবি******************)
শরীকদ্বয়ের প্রতি আল্লাহর সাহায্য থাকে, যতক্ষণ না তাতে একজন অপর জনের সাথে অবিশ্বাসের কাজ করবে। যদি একজন অপর জনের সাথে খিয়ানত করে, তহলে আল্লাহ্ সে সাহায্য তুলে নেন ও বন্ধ করে দেন।
রাসূলে করীম (সা) আল্লাহর কথা উদ্ধৃত করেছেন এ ভাষায়ঃ ( আরবি******************)
দুই শরীকী কারবারীদের মধ্যে আমি তৃতীয়, যতক্ষণ একজন অপরজনের খিয়ানত করবে না। যদি একজন অপর জনের খিয়ানত করে তাহলে আমি তাদের দুজনের মধ্য থেকে বের হয়ে যাই আর সেখানে শয়তান এসে যায়।
বীমা কোম্পানী
ব্যবসায়ের এক অতি আধুনিক রূপ হচ্ছে বীমা কোম্পানী। বীমা নানা রকমের হয়ে থাকে। জীবন-বীমা, দুর্ঘটনা বীমা, অগ্নি বীমা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। কিন্তু এ ব্যাপারে ইসলামী শরীয়তের হুকুম কি, তা-ই আলোচ্য। ইসলামে কি এ ধরনের ব্যবসা চলতে দেয়া হবে? এ প্রশ্নের জবাবের পূর্বে বীমা কোম্পানীসমূহের প্রকৃতি জানতে হবে। বীমা যে করায় বীমা কোম্পানীর সাথে তার সম্পর্ক কি ধরনের হয়, তাও জানা আবশ্যক। অন্য কথায়, বীমাকারী কি কোম্পানীর মূল সংস্থায় একজন অংশীদার হিসেবে বিবেচিত? যদি তা-ই হয় তাহলে বীমাকারীকে মূল ব্যবসায়ের লাভ লোকসানে সমানভাবে শরীক হতে হবে। দুর্ঘটনা সংক্রান্ত বীমায় বীমাকারীকে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা বার্ষিক হিসাবে কোম্পানীকে দিয়ে দিতে হয়। যে ব্যবসায়ের বীমা করানো হয়েছে, তা যদি কোন দুর্ঘটনার শিকার না হয়, তাহলে সে ব্যবসায়ের মালিককে দেয়া সব টাকাই কোম্পানী নিয়ে নেবে ও হজম করে ফেলবে, তা থেকে কিছু ফেরত দেয়া হবে না। অবশ্য দুর্ঘটনা কবলিত হলে নির্ধারিত পরিমাণ টাকা ক্ষতিপূরণ বাবদ আদায় করা হয়। কিন্তু এ ব্যবস্থা শরীকদারী কারবার বা ব্যবসায়ের প্রতিকৃতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।
জীবন বীমার নিয়ম হচ্ছে, যদি দুই হাজার টাকার বীমা করানো হয় এবং প্রথম কিস্তি দিয়ে দেয়ার পর মৃত্য সঙ্ঘটিত হয়, তাহলে বীমাকারী ব্যক্তি পূর্ণ দুই হাজার টাকা পাওয়ার অধিকারী কিন্তু সে যদি মূল ব্যবসায়ের অংশীদারের মতো হতো, তাহলে দেয়া কিস্তির পরিমাণ টাকা ও সেই হারে মুনাফাটুকুই তার পাওয়া উচিত। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, বীমাকারী যদি কোম্পানীর নিয়মাবলী লংঘন করে ও কিস্তি দিতে অক্ষম হয়, তাহলে দেয়া সব টাকা বা তার অংশ-বিশেষ থেকে বঞ্চিত থাকতে হবে। আর এ নিয়মটা যে অন্যায়, জুলুম ও অসত্য শর্ত, তা বলাই বাহুল্য।
আর উভয় পক্ষ যদি নিজ নিজ সম্মতিক্রমে এ শর্ত মেনে নেয় এবং এরূপ চুক্তিতে আবদ্ধ হয়- নিজ নিজ স্বার্থ ভাল করে বুঝে-শুনেই হোক-না কেন, তবু তা জায়েয হবে না। কেননা সুদখোর ও সুদ গ্রহীতারাও পারস্পরিক সম্মতিক্রমেই এ চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। জুয়া খেলে যারা, তাদেরও পারস্পরিক সম্মতি থাকে, তাতেই হারাম কখনই হালাল হয়ে যেতে পারে না। এ ধরনের সম্মতি গ্রহণযোগ্য নয়। এটা এমন নয় যে, এতে ধোঁকাবাজি ও সীমালংঘনের সামান্য অংশও নেই। এতে এক পক্ষের মুনাফা নিশ্চিত আর অন্য পক্ষের লাভবান হওয়া সম্পূর্ণ অনিশ্চিত। এসব ক্ষেত্রে আসল ভিত্তি হতে হবে সম্পূর্ণ নির্ভেজাল সুবিচার ও ন্যায়পরতা। সর্ব ব্যাপারেই তা এমনভাবে নিশ্চিত হতে হবে যে, না নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হবে, না অন্যরা ক্ষতির মধ্যে পড়বে।
বীমা কোম্পানী কি পারস্পরিক সাহায্য সংস্থা
বীমাকারী ও বীমা কোম্পানীর মধ্যে সম্পর্ক অংশীদারী কারবারের মতো নয়। তাহলে সে সম্পর্কের রূপটা কি? তাদের মধ্যে পারস্পরিক সাহায্যের সম্পর্ক কি এটা? এসব প্রতিষ্ঠান কি পারস্পরিক সাহায্য সংস্থা যা দানকারীদের সহযোগিতা বা অংশীদারিত্বে চালান হয়? আর আর্থিক অংশীদারিত্ব হয় পরস্পরের সাহায্য করার উদ্দেশ্যে?...তা যে নয়, তাতো সুস্পষ্ট।
পারস্পরিক সাহায্যের জন্যে নির্ভুল কর্মপন্থা গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়। বিপন্ন লোকদের সাহায্য করা তার লক্ষ্য হওয়া উচিত এবং এ উদ্দেশ্যেই অর্থ জমা হওয়া উচিত। এজন্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবেঃ
১. ব্যক্তি নির্দিষ্ট পরিমাণ চাঁদ ভ্রাতৃত্বের খাতিরে দান হিসেবে দেবে এবং এ ফাণ্ড থেকে কেবলমাত্র প্রয়োজন ক্লিষ্ট ব্যক্তিদের সাহায্য করতে হবে।
২. ফণ্ড থেকে উপকৃত হওয়ার জন্যে কেবলমাত্র বৈধ পন্থাই অবলম্বন করতে হবে।
৩. কেউ যেন এ উদ্দেশ্যে দান না দেয় যে, দুর্ঘটনা সঙ্ঘটিত হলে সে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ লাভ করবে। বরং প্রতিষ্ঠানের ফাণ্ড থেকে সাধ্যমত একটা দেয়ার ব্যবস্থা থাকতে হবে, যেন তা দিয়ে সম্পূর্ণ বা যথেষ্ট পরিমাণে ক্ষতিপূরণ হয়ে যায়। ( আরবি******************)
৪. দান দানই। তা ফেরত নেয়া সম্পূর্ণ হারাম। কাজেই যখন কোন দুর্ঘটনা ঘটবে তখন তাতে শরীয়তের বিধান অনুযায়ী বিচার বিবেচনা করতে হবে।
এ শর্তসমূহ কেবলমাত্র এমন কতিপয় সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের ওপরই প্রযোজ্য হতে পারে, যা ঠিক এ উদ্দেশ্যেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাতে ব্যক্তিরা দান হিসেবে নিজেদের মাসিক অংশ আদায় করে দেবে, তা ফেরত নেয়ার তাদের কোন অধিকার থাকবে না। এ শর্ত ধার্য থাকে না যে, বিপদকালে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা তাদের পেয়ে যেতে হবে।
কিন্তু বীমা কোম্পানীসমূহ এবং বিশেষ করে জীবন বীমায় নিম্নোক্ত শর্তসমূহ আদৌ আরোপ করা হয় না। তার অবস্থা সম্পর্ণ স্বতন্ত্র।
১. বীমাকারীরা (policy Holdders) দান হিসেবে কিস্তি দেয় না। তার চিন্তাও তাদের মনে জাগে না।
২. বীমা কোম্পানীসমূহ নিজেদের মূলধন হারাম সুদী করবারে বিনিয়োগ করে মুনাফা কামাই করে। কিন্তু কোন মুসলমানই সুদী কারবারে শরীক হতে পারে না। এ ব্যাপারে সুবিধাবাদী ও কঠোরতাবাদী সকলেই একমত।
৩. বীমাকারী চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার পর সমস্ত কিস্তির টাকা ফেরত নিয়ে নেয়। সেই সাথে সে আরও অতিরিক্ত টাকা পেয়ে যায়। তা হলে এ অতিরিক্ত টাকা সুদ ছাড়া আর কি মনে করা যেতে পারে?
অনুরূপভাবে ধনী সামর্থবান ব্যক্তিকে অভাবগ্রস্ত দরিদ্র ব্যক্তির তুলনায় বেশি টাকা দেয়াও পারস্পরিক সাহায্যমূলক ভাবধারার সম্পূর্ণ বিপরীত। কেননা দেখা যায়, অর্থশালী ব্যক্তি মোটা টাকার বীমা করায়। এ জন্যে মৃত্যু বা দুর্ঘটনা কালে তাকে সেই অনুপাতে অনেক বেশি টাকা দেয়া হয়। কিন্তু সাহায্য করার ভাবধারা টাকা দেয়া হবে।
৪. যে ব্যক্তি বীমার চুক্তি শেষ করতে ইচ্ছুক হয়, তাকে দিয়ে দেয়া অংশের টাকায় বড় ক্ষতি স্বীকার করতে হয়। কিন্তু এরূপ ক্ষতি স্বীকার করার শরীয়তের দৃষ্টিতে কোন বৈধ কারণ নেই।
পরিবর্তন ও সংশোধনী
এ সব সত্ত্বেও বর্তমানে প্রচলিত দুর্ঘটনা সংক্রান্ত বীমা ব্যবস্থার সংশোধন করে তাকে ইসলামী নিয়ম নীতির খুব কাছাকাছি নিয়ে আসা সম্ভবপর। আর তার জন্যে এ ব্যবস্থা নিতে হবে যে, বিনিময়ের শর্তের ভিত্তিতে দানসমূহ গ্রহণ করার নীতি অবলম্বন করতে হবে। বীমাকারী কোম্পানীকে আর্থিক সাহায্য দেবে এ শর্তে যে, দুর্ঘটনা ঘটলে কোম্পানী তাকে ক্ষতিপূরণ দেবে, তাতে তার সাহায্য হয়ে যাবে, বিপদের মাত্রা লাঘব হবে। কোন কোন ফিকহী মতে এরূপ চুক্তি জায়েয। বীমার ক্ষেত্রে যদি এরূপ পরিবর্তন ও সংশোধনী কার্যকর করে নেয়া হয় আর বীমা কোম্পানীসমূহের কার্যাদি সুদমুক্ত হয়, তাহলে তা জায়েয হবে বলে মনে করা যায়। কিন্তু জীবন-বীমার সমস্ত ব্যাপার শরীয়তের বিধান থেকে অনেক অনেক দূরে অবস্থিত।
ইসলামে বীমা পদ্ধতি
বীমা কোম্পানীসমূহ বর্তমানে ইসলামী বিধান অনুযায়ী চলছে না, তা আমরা দেখতে পেলাম। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, মূল বীমা ব্যাপারটাই বুঝি ইসলামের পরিপন্থী। আসলে তা নায়। তার বর্তমান প্রচলিত নীতিগুলোই শুধু ইসলামের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ, এ হচ্ছে আসল কথা। তাতে যদি ইসলাম অনুকূল নিয়ম-নীতি অবলম্বন করা হয়, তাহলে তা ইসলামের দৃষ্টিতে অবশ্যই গ্রহণযোগ্য হবে।
সত্যি কথা এই যে, ইসলামী জীবন-বিধান মুসলিম জনগণ ও ইসলামী রাষ্ট্রের অধীন বসবাসকারী লোকদের জন্যে সামষ্টিক ভরণ-পোষণ ব্যবস্থা বা সরকারী অর্থ ভাণ্ডার তথা বায়তুলমালের সাহায্যে বীমার নিরাপত্তা ব্যবস্থা কার্যকর করেছে। ইসলামের বায়তুলমাল প্রকৃতপক্ষে জনগণের জন্যে বীমা কোম্পানিই বটে। যারাই তার অধীন বসবাস করবে তাদের সকলের জন্যেই তা কাজে আসবে।
দুর্ঘটনা ও বিপদ-আপদকালে ব্যক্তিদের সাহায্য সহযোগিতা করার দায়িত্ব ইসলাম গ্রহণ করেছে। কেউ যদি বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়ে তবে সে সরকারী দায়িত্বশীলের কাছে নিজের সমস্যা পেশ করতে পারে। সরকার সেই অনুযায়ী তার ক্ষতিপূরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। মৃত্যুর পর অসহায় উত্তরাধিকারীদের জন্যেও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে।
নবী করীম (সা) ইরশাদ করেছেনঃ ( আরবি******************)
প্রত্যেকটি মুসলিমের সাথে আমার সম্পর্ক তার নিজের তুলনায়ও অনেক বেশি নিকটবর্তী। যে মুসলমান ধন-মাল রেখে যাবে তা তার উত্তরাধিকারীই পাবে। আর যে লোক ঋণ বা অক্ষম শিশু সন্তান রেখে যাবে সেই ঋণ শোধ ও শিশুদের লালন-পালনের ব্যবস্থা করার দায়িত্ব আমার ওপরই বর্তিবে।
ইসলাম মুসলিম জনগণের জন্যে যে গুরুত্বপূর্ণ নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে, তা হচ্ছে ফরয যাকাত ব্যয়ের জন্যে নির্দিষ্ট করা ক্ষেত্র ( আরবি******************) ঋণগ্রস্ত লোকগণ। পূর্বকালের কোন কোন তাফসীরকার এ শব্দের ব্যাখ্যায় বলেছেনঃ ( আরবি******************)
যার ঘরবাড়ি সব পুড়ে গেছে কিংবা বন্যা-বাদল যার সব ধন-সম্পদ ভাসিয়ে নিয়ে গেছে সে-ই এ গারেমীন-এর মধ্যে গণ্য।
কৃষি জমিতে ফসল উৎপাদন
মুসলমান কৃষি জমির মালিকানা শরীয়ত মুতাবিক লাভ করলে সে জমি চাষ করে ফসল লভ করা বা গাছপালা লাগিয়ে ফল ফলাদি হাসিল করা তার একান্ত কর্তব্য হয়ে পড়ে। বিনা চাষে জমিকে বেকার ফেলে রাখা ইসলামে অবৈধ কাজ। কেননা তা করা হলে আল্লাহর দেয়া নিয়ামতের প্রতি অবজ্ঞা দেখানো হবে। ধন-সম্পত্তির অপচয়ও বলা যায় তাকে। অথচ নবী করীম (সা) ধন-সম্পত্তি বিনষ্ট করতে স্পষ্ট ভাষায় নিষেধ করেছেন। জমি মালিক জমি থেকে উপকৃত হওয়ার জন্যে নানাবিধ পন্থা ও প্রক্রিয়া অবলম্বন করতে পারে।
জমি কাজে লাগাবার নানা উপায়
জমির মালিক নিজেই জমি চাষাবাদ করবে। গাছপালা লাগিয়ে তাতে পানি সেচ করার সুষ্ঠ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। তার ফলে সে জমিতে ফসল ফলবে বা গাছ পালায় ফলন ধরবে। এটা বস্তুতই খুব পছন্দনীয় কাজ। যেসব মানুষ, পাখি ও জীবজন্তু এসব ক্ষেত বাগান থেকে উপকৃত হবে, তার সওয়াব সেই মালিকই পাবে। রাসূলে করীম (সা)-এর বড় বড় সাহাবী যে কৃষি ও বাগান রচনার কাজ করেছেন, তা তো সকলেই জানা কথা।
দ্বিতীয় পন্থা
জমি মালিক নিজ জমি চাষাবাদ করতে পারছে না। তখন সে নিজের জমি এমন ব্যক্তিকে ধার হিসেবে দিয়ে দেবে, যে নিজের যন্ত্রপাতি, শ্রমিক, বীজ ও জন্তু লাগিয়ে চাষাবাদের কাজ সম্পন্ন করবে। কিন্তু জমি মালিক নিজে তা থেকে কিছুই নেবে না। এভাবে ধারে জমিদান ইসলামে কাম্য ও প্রশংসিত। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলে করীম (সা) বলেছেনঃ ( আরবি******************)
যার জমি আছে, সে নিজে তা চাষাবাদ করবে, নতুবা তার ভাইকে তা চাষাবাদের জন্যে দিয়ে দেবে।
হযরত জাবির (রা) বর্ণিত, তিনি বলেছেনঃ ( আরবি******************)
আমরা নবী করীম (সা)-এর যুগে ‘মুজাবিরাত’ নিয়মে জমি চাষাবাদ করতাম। ফলে আমরা কাটাই হওয়ার পর শীষের মধ্যে অবশিষ্ট দানাগুলো এখান-ওখান থেকে পেয়ে যেতাম। তখন নবী করীম (সা) বললেনঃ যার জমি আছে, সে যেন নিজে তা চাষাবাদ করে কিংবা তার ভাইকে বিনিময় ব্যতিরেকেই চাষ করতে দিয়ে দেয়। আর তা-ও না করলে তা ছেড়ে দেবে।
‘মুজাবিরাত’ অর্থ জমির একাংশের ভিত্তিতে তা চাষাবাদ করা।
কোন কোন লোক এ হাদীসের বাহ্যিক অর্থের ভিত্তিতে বলেছেন, জমি দ্বারা উপকার গ্রহণের এ দুটি পন্থাই শরীয়তসম্মত, হয় নিজেই তা চাষ করবে নতুবা কোনরূপ মূল্য বা বিনিময় ছাড়াই কাউকে জমি চাষ করতে দিয়ে দেবে। আর তা হতে পারে এভাবে যে, জমি হবে তার, যে তার মালিক আর ফসল হবে তার, যে তার চাষাবাদ করবে।
( আরবি******************)
টাকা বা পয়সার বিনিময়ে জমি লাগিয়ে দেয়া ঠিক নয়। অন্য কোন প্রকান চুক্তিতেও জমি দেয়া যায় না। শুধু একটি উপায়ই আছে। হয় মালিক নিজে তা চাষাবাদ করবে, না হয় কোনরূপ বিনিময় ছাড়াই অন্যকে তা দিয়ে দেবে।
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, এ সব হাদীসে জমি দিয়ে দিতে যে বলা হয়েছে, তার অর্থ এ নয় যে, দিয়ে দেয়া ওয়াজিব। আসলে তা মুস্তাহাব মাত্র। এভাবে দিয়ে দেয়াটা বেশ পছন্দনীয় কাজ। আমার ইবনে দীনার থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেনঃ হযরত ইবনে আব্বাসের প্রখ্যাত ছাত্র তায়ূসকে জিজ্ঞেস করলামঃ আমি যদি ‘মজাবিরাত’ (জমি ভাগে চাষ) পরিহার করি, তাহলে কেমন হয়? জবাবে তায়ূস বললেনঃ সবচেয়ে বড় আলিম হযরত ইবনে আব্বাস (রা) আমাকে বলেছেন যে, নবী করীম (সা) তা নিষেধ করেন নি। তিনি কথাটি বলেছেন এভাবেঃ ( আরবি******************)
তোমরা নিজের ভাইকে বিনিময় ছাড়াই জমি দিয়ে দেয়া তার কাছ থেকে ‘কর’ আদায় করার চেয়ে উত্তম। (বুখারী)
ভাগে জমি চাষ
তৃতীয় পন্থা হচ্ছে, যে লোক নিজের যন্ত্রপাতি বীজ ও জন্তু দ্বারা চাষের কাজ করবে, জমি মালিক তাকে জমি দেবে এ শর্তে যে, জমি ফসলের উভয়ের সম্মত পরিমাণ অংশ যেমন অর্ধেক বা এক-তৃতীয়াংশ সে পাবে। জমি মালিক জমি চাষকারীকে বীজ যন্ত্রপাতি ও জন্তু দিলে তাও জায়েয হবে। এ পন্থায় জমি চাষাবাদে ব্যবস্থা করলে তাকে পারস্পরিক জমি চাষ, ভাগে জমি চাষ, মুখাবিরা, মুসাকাত ইত্যাদি বলা হয়।
নবী করীম (সা) নিজে খায়বরের জমি অর্ধেক ফসলের শর্তে চাষ করতে দিয়েছিলেন। (বুখারী, মুসলিম) এ ধরনের পারস্পরিক ‘চাষাবাদকে’ যে সব ফিকাহবিদ জায়েয মনে করেন, রাসূলে করীম (সা)-এর উপরিউক্ত কাজ তাঁদের দলিল। তাঁরা বলছেনঃ এ এক প্রখ্যাত সর্বজনপরিচিত ও সহীহ ব্যাপার। রাসূলে করীম (সা) জীবনভর মৃত্যু পর্যন্ত এ পন্থায় আমল করেছেন। তাঁর পরবর্তীকালের লোকেরাও তা-ই করেছেন। তার পরে খুলাফায়ে রাশেদুনও শেষ পর্যন্ত তাঁরই পদাংক অনুসরণ করেছেন। মদীনার এমন কোন ঘরই ছিল না, যে ঘরের লোকেরাও এ পন্থায় চাষাবাদের কাজ করেন নি। নবী করীম (সা)-এর বেগমরা এ নীতিরই অনুসরণ করেছেন। এ এমন একটা ব্যাপার যা নাকচ বা প্রত্যাহার করা যেতে পারে না। কেননা প্রত্যাহার বা নীতি বদল তো কেবলমাত্র নবী করীম (সা)-এর জীবদ্দশাতেই হতে পারত। কিন্তু যে কাজ তিনি মৃত্যু পর্যন্ত করলেন, তাঁর পর খলীফাগণও করলেন, সাহাবিগণ যে ব্যাপারে সম্পূর্ণ একমত ও সর্বসম্মতভাবে আমল করেছেন, একজনও যে নীতি বিরোধিতা বা প্রতিবাদ করেন নি, তা কি করে পরিত্যাক্ত ও নাকচ হয়ে যেতে পারে? আর রাসূলে করীম (সা)-এর জীবদ্দশায়ই যদি তা পরিত্যক্ত হয়ে থাকে, তাহলে তার পর তাঁর অনুসারী লোকেরা এ পন্থায় কি করে চাষাবাদ করলেন? এ বিষয়টি গোপন থাকলই বা কি করে যে, খুলাফায়ে রাশেদুন পর্যন্ত তা জানলেন না? অথচ খায়বারের ব্যাপারটি তো সর্বজনবিদিত। পরিত্যক্ত পওয়ার কথা যিনি বর্ণনা করেন তিনি-ই বা তখন কোথায় ছিলেন যে, তিনি কাউকে কিছু জানালেন না? ( আরবি******************)
ভুল নীতিতে পারস্পরিক চাষাবাদ
নবী করীম (সা)-এর সময়ে আর এক ধরনের চাষাবাদ প্রচলিত ছিল। কিন্তু তাতে ধোঁকা, প্রতারণা ঠকবাজি ও অজ্ঞতার অবকাশ ছিল, যার দরুন পক্ষদ্বয়ের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদের সৃষ্টি হতো। এজন্যে নবী করীম (সা) চাষাবাদের এ পন্থাকে নিষেদ্ধ ঘোষণা করেন। দ্বিতীয়ত, ইসলাম সুস্পষ্ট ন্যায়পরতা ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতে চায়; কিন্তু উপরিউক্ত পন্থায় চাষাবাদে সেই ন্যায়পরতা ও ইনসাফের পরিপন্থী কাজ হলেই তিনি তা নিষেধ করতে বাধ্য হয়েছিলেন।
সে পন্থা ছিল এই যে, জমি মালিক চাষকারীর উপর এ শর্ত চাপিয়ে দিত যে, নির্দিষ্ট জমির এক-চতুর্থাংশ তার জন্যে নির্দিষ্ট করে দেয়া হবে ও তা সীমা নির্ধারণ করে দেয়া হবে। সমগ্র চাষের !ব্দর সে সেই নির্দিষ্ট জমিটুকুরই ফসল পাবে, তা যতটাই হোক। অথবা একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ ফসল মাপা বা ওজন করা সে পাবে। আর অবশিষ্ট ফসল থাকবে একা চাষকারীর জন্যে, অথবা তা দুজসের মধ্যে আধা-আধি ভাগ করে দেয়া হবে।
কিন্তু নবী করীম (সা) দেখলেন যে, ন্যায়পরতা ও সুবিচারের দাবি হচ্ছে এই যে, সর্বমোট ফসলেই- তা কম হোক বেশি হোক, উভয় পক্ষকে শরীক হতে হবে। তাদের দুজনের একজনের জন্যে একটা পরিমাণ জমি বা ফসল পূর্বেই নির্দিষ্ট হয়ে যাওয়া ঠিক কাজ নয়। কেননা অনেক সময় জমির সেই অংশ হয়ত কোন ফসলই দিল না। তাহলে তো একজনই মাত্র যা পাওয়ার পেয়ে যাবে। আর অপর জন প্রতারিত ও বঞ্চিত হয়ে থাকবে। কেননা নির্দিষ্ট খণ্ড জমিতে হয়ত কোন ফসলই ফললো না। তাহলে সে তো কিছুই পেল না অথচ অপর পক্ষ পুরোপুরি পেয়ে গেল। এরূপ অবস্থায় ইনসাফ পূর্ণ পন্থা এই হতে পারে যে, পারস্পরিক চুক্তি অনুযায়ী সমস্ত জমির সমস্ত ফসল থেকেই প্রত্যেক পক্ষ নিজ অংশ গ্রহণ করবে। যদি জমির ফসল বেশি হলো তাহলে তার ফায়দা উভয় পক্ষই পেলো। আর যদি কম হয় তাহলে উভয়ই কম কম করে পেয়ে গেল। আর যদি কোন ফসলই না হয়, সে বঞ্চনায়ও উভয় পক্ষই শরীক থাকবে। পক্ষদ্বয়ের জন্যে এ পন্থাই যে উত্তম, তাতে কোন সন্দেহ নেই।
হযরত রাফে ইবনে খদীজ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেনঃ ( আরবি******************)
আমাদের মধ্যে যাদের জমি ছিল তারা বেশির ভাগ পারস্পরিক চাষাবাদের নীতিতে কাজ করত। তারা জমি এ শর্তে কেরায়া দিত যে, তার এক কোণের জমির ফসল জমির মালিকের জন্যে নির্দিষ্ট করা হতো। কিন্তু অবস্থা এই হতো যে, জমির সেই নির্দিষ্ট অংশে কোন ফসল হতো না, হতো অপর ভাগে। আর কখনও জমির সেই নির্দিষ্ট অংশে ফসল হতো অপর অংশে হতো না। এই কারণে এ রূপ চাষাবাদের কাজ করতে আমাদের নিষেধ করে দেয়া হয়।
এই হযরত রাফে বলেছেনঃ ( আরবি******************)
নবী করীম (সা)-এর লোকেরা খালের কিনারে ও পানি প্রবাহের মুখের স্থানে ফল-ফসলের শর্তে চাষাবাদের চুক্তি করত কিংবা ফসল থেকে কিছু দেয়ার বিনিময়ে করত। পরে দেখা যেত এ অংশের ফসল নষ্ট হয়েছে, এ অংশের ফসল রক্ষা পেয়েছে অথবা এর বিপরীতটা হতো। আর লোকদের জন্যে এ পন্থা ভিন্ন জমি লাগানো আর কোন নিয়ম ছিল না। এ কারণে তা নিষেধ করা হয়। (মুসলিম)
নবী করীম (সা) জিজ্ঞেস করলেনঃ ( আরবি******************)
তোমাদের চাষের জমি-ক্ষেত লাগান-পরানের কাজ তোমরা কিভাবে কর?
লোকেরা বললঃ ( আরবি******************)
আমরা এক-চতুর্থাংশ এবং খেজুর ও গমের একটা পরিমাণের বিনিময়ে পারস্পরিক চাষের চুক্তি করি।
এ কথা শুনে তিনি বললেনঃ তোমরা তা করবে না। এর অর্থ তখন একটা নির্দিষ্ট মাপের পরিমাণ ঠিক করে দিত, তারা তার ওপর থেকে নিয়ে নিত। পরে চাষকারীদের মধ্যে অবশিষ্ট ফসল ভাগ করা হতো। কেউ এক-চতুর্থাংশ কেউ চার ভাগের তিন ভাগ নিয়ে নিত।
এসব ঘটনা থেকে স্পষ্টভাবে জানা যায় যে, নবী করীম (সা) তাঁর প্রতিষ্ঠিত সমাজে পূর্ণাঙ্গ ও সর্বাত্মক সুবিচার ও ন্যায়পরতা প্রতিষ্ঠার জন্যে বিশেষভাবে উদগ্রীব থাকতেন। আর যে যে কারণে পারস্পরিক ঝগড়া-বিসম্বাদের সৃষ্টি হতে পারে বলে আশংকা করতেন, তিনি মুমিনদের সমাজ থেকে সেই সবকিছু দূর করে দিতে বদ্ধপরিকর ছিলেন।
হযরত যায়দ ইবনে সাবিত (রা) বর্ণনা করেছেনঃ নবী করীম (সা)-এর সামনেই দুই ব্যক্তি জমি নিয়ে ঝগড়া করল। তখন তিনি বললেনঃ ( আরবি******************)
তোমাদের অবস্থা যদি এ-ই হয়ে থাকে, তাহলে তোমরা চাষ জমি ভাড়ায় দিও না।
অতএব প্রত্যেক জমি মালিকের উচিত তার সঙ্গী ও সাথীর প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ও মর্যাদা দানকারী হওয়া। এজন্যে জমি মালিক যেন ফসলের বেশির ভাগই দাবি করে না বসে। পক্ষান্তরে চাষকারীও জমি মালিককে তার জমির দিক দিয়ে ক্ষতিগ্রস্থ না করে। এ প্রেক্ষিতে হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত হয়েছেঃ ( আরবি******************)
পারস্পরিক ভিত্তিতে জমি চাষাবাদ করাকে নবী করীম (সা) হারাম করে দেন নি। বরং তিনি তো পক্ষদ্বয়ের প্রত্যেককে অপরের প্রতি সহানুভূতিপূর্ণ আচরণ অবলম্বন করতে বলেছেন। (তিরমিযী)
এজন্যে তায়ূসকে যখন বলা হলো, হে আবূ আবদুর রহমান! এ ‘মুখাবিরা’ যদি ত্যাগ করি তাহলে তো ভাল হয়। কেননা লোকেরা মনে করে যে, নবী করীম (সা) তা করতে লোকদের নিষেধ করেছেন। তখন তিনি বলেছিলেনঃ
আমি তাদের সাহায্য করব, আমি তাদের দেব।
তারা নিজেদের জমি থেকে বেশি বেশি কামাই করার চিন্তিই করত না। যারা জমিতে শ্রম-মেহনত করে, তারা ক্ষুধায় কাতর হয়ে থাক, তা-ই তারা চাইত না। বরং তারা তাদের সাহায্য করত, তাদের দিত। আর বস্তুত এই হচ্ছে মুসলিম সমাজের বৈশিষ্ট্য।
অনেক সময় জমি মালিক জমিকে বেকার ফেলে রাখে। তাতে চাষাবাদও করে না, গাছ-পালাও লাগায় না। কিন্তু কোন চাষাবাদকারীকেও স্বল্প বিনিময়ে জমি দিতে প্রস্তুত হয় না। এ কারণে পযরত উমর ইবনে আবদুল আজীজ তাঁর খিলাফতের বিভিন্ন দায়িত্বশীলদের নির্দেশ দিয়েছিলেনঃ এক-চতুর্থাংশ বা এক-তৃতীয়াংশ অথবা এক-পঞ্চমাংশ ফসলের বিনিময়ে লোকদের জমি চাষ করতে দাও, দশমাংশ পর্যন্তও দিতে বলেছিলেন এবং জমিকে অনাবাদী করে রাখতে নিষেধ করেছিলেন।
নগদ টাকায় জমি লাগানো
চতুর্থ পন্থা এই হতে পারে যে, চাষাবাদকারীকে জমি চাষ করতে দেয়া হবে এ শর্তে যে, সে নগদ টাকায় মূল্য আদায় করবে।
বহু প্রখ্যাত ফিকাহবিদই এ পন্থাকে জায়েয বলেছেন। অবশ্য অপর কিছু সংখ্যক ফিকাহবিদ তা নিষেধ করেছেন। তাঁদের দলিল হচ্ছে নবী করীম (সা) জমি কেরায়ায় দিতে নিষেধ করেছেন- এটি সহীহ্ বর্ণনা। হযরত আবূ বকর, হযরত উমর, হযরত রাফে ইবনে খদীজ, হযরত জাবির, আবূ সায়ীদ, আবূ হুরায়রা ও ইবনে উমর (রা) এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তাঁরা সকলেই বলেন যে, নবী করীম (সা) জমিকে কেরায়ায় লাগাতে অকাট্যভাবে নিষেধ করেছেন।
( আরবি******************)
জমি কেরায়া লাগানোর ভিন্নতর পন্থা ভাগে চাষ করানো। নবী করীম (সা) তাঁর জীবদ্দশায় খায়বর অধিবাসীদের সাথে এ চুক্তিই করেছেলেন এবং তার ওপর তিনি শেষ পর্যন্ত অবিচল রয়েছিলেন। খুলাফায়ে রাশেদুনের আমলেও তার ব্যতিক্রম কিছু করা হয় নি।
এ পর্যায়ে ইসলামী আইনের ক্রমবিবর্তন যারা লক্ষ্য করেছেন, তাঁদের কাছে ইবনে হাজমের কথার যথার্থতা খুবই স্পষ্ট হয়ে থাকবে। তিনি লিখেছেন, নবী করীম (সা) যখন তাদের মধ্যে উপস্থিত হলেন, তখন তাঁরা তাঁদের চাষের জমি কেরায়ায় লাগাতেন। রাফে ইবনে খদীজ (রা) থেকেও অনুরূপ বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে। আর জমি কেরায়ায় লাগানোর ব্যাপারটা রাসূলে করীম (সা)-এর উপস্থিতির পূর্বেও যেমন চলত, তার পরও তাতে পরিবর্তন আসেনি। এ ব্যাপারে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিই বিন্দুমাত্র সন্দেহ করতে পারেন না। এরপর হযরত জাবির, আবূ হুরায়রা, আবূ সায়ীদ, রাফে, যহীর (রা) ও বদর যুদ্ধে শরীক হওয়া সাহাবী এবং হযরত ইবনে উমর (রা) থেকে সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছেঃ ( আরবি******************)
নবী করীম (সা) জমি কেরায়া লাগাতে সার্বিকভাবে নিষেধ করেছেন।
এ হাদীসের দ্বারা পূর্বের মুবাহ নীতি যে বাতিল হয়ে গেল, তাতেও কোন সন্দেহ নেই। অতএব নগদ টাকায় জমি কেরায়া লাগানো যাঁরা জায়েয বলেন, তাঁরা ভুল কথা বলেন। তাঁদের কথা কখনই সহীহ প্রমাণিত হতে পারে না। তবে উৎপন্ন ফসলের নির্দিষ্ট অংশ দেয়ার বিনিময়ে তা কেরায়ায় লাগানো যায়েয হতে পারে। কেননা নবী করীম (সা) থেকে এবথা প্রমাণিত যে, তিনি কেরায়ায় জমি লাগাতে নিষেধ করার পর খায়বরে ফসলের ভাগের ভিত্তিতে জমি চাষ করে দেয়ার চুক্তি করেছিলেন এবং তার মৃত্যু পর্যন্ত এ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ অপরিবর্তীত ছিল। ( আরবি******************)
প্রাথমিককালের অনেক ফিকাহবিদই এ মত পোষণ করতেন। ইয়েমেনের প্রখ্যাত ফিকাহবিদ ও মহামান্য তাবেয়ী তায়ূস স্বর্ণ-রৌপ্যের বিনিময়ে জমি চাষ করতে দেয়াকে মাকরূহ মনে করতেন। কিন্তু ফসল ভাগে দেয়ায়- তা এক তৃতীয়াংশ হোক বা চতুর্থাংশ- কোন দোষ মনে করতেন না। কেউ কেউ যখন এ বিষয়ে আপত্তি প্রকাশ করলেন এবং বললেন যে, নবী করীম (সা) জমি কেরায়া লাগাতে নিষেধ করেছেন, তখন তিনি বললেনঃ আমাদের কাছে হযরত মু’আয উপস্থিত হলেন- নবী করীম (সা)-ই তাঁকে ইয়েমেনে পাঠিয়েছিলেন, তখন তিনি এক-তৃতীয়াংশ বা এক-চতুর্থাংশ ফসলের শর্তে জমি চাষ করতে দিয়েছিলেন। আর আজ পর্যন্ত তাই করে যাচ্ছি।
এ থেকে বোঝা যায়, তায়ূসের মতে নগদ মূল্যে জমি কেরায়া লাগানোই নিষেধ। তবে ফসল ভগের শর্তে জমি চাষ করতে দেয়ায় কোন অসুবিধা নেই।
মুহাম্মদ ইবনে সিরীন, কাসেম ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবূ বকর সিদ্দীক থেকেও এ কথাই জানা গেছে। তবে তাবেয়ীনের মধ্য থেকে কিছু লোক জমি যে-কোন ভাবে কেরায়ায় দেয়াকে নিষিদ্ধ বলে মনে করেন, তা নগত মূল্যেই হোক আর ফসল ভাগের ভিত্তিতেই হোক। কিন্তু এ মত খুব বলিষ্ঠ নয়। কেননা নবী করীম (সা) খূলাফায়ে রাশেদুন ও হযরত মু’আয (রা) নিজেরা ফসল ভাগের শর্তে জমি চাষাবাদ করেছেন, করিয়েছেন। তাতে এই পন্থার জায়েয হওয়ার কথা নিঃসন্দেহে জানা যায়। প্রাক্তন কালসমূহে মুসলমানদের জন্যে কার্যত এ নীতি অনুযায়ীই আইন প্রণয়ন করা হতো। তবে নগদ মূল্যের বিনিময়ে জমি কেরায়ায় দেয়া যে নিষেধ, তা হাদীস থেকেই প্রমাণিত। আর তা যে যুক্তিসঙ্গত, তাও নিঃসন্দেহ।
নগদ মূল্যে জমি লাগানো নিষিদ্ধ হওয়ার যৌক্তিকতা
ইসলামের মৌলনীতি ও আদর্শের দৃষ্টিতে চিন্তা-বিবেচনা করলে খালি জমি নগদ টাকার বিনিময়ে লাগানো নাজায়েয হওয়াই বাঞ্ছনীয় মনে হবে।
ক. নবী করীম (সা) উৎপন্ন ফসলের একটা নির্দিষ্ট অংশের বিনিময়ে জমি কেরায়া লাগাতে নিষেধ করেছেন। কেবলমাত্র ফসলের হারের ভিত্তিতে লাগানোটাই জায়েয অর্থাৎ উৎপাদনের তিন ভাগের এক ভাগ বা চার ভাগের একভাগের ভিত্তিতে জমি লাগানো যেতে পারে। শতকরা হারে (percentage) ভাগ ঠিক করলে খুবই ভাল হয় বলে আমরা মনে করি। তাহলে উৎপন্ন ফসলের অংশ লাভ করার ব্যাপারে উভয় পক্ষই সমানভাবে উপকৃত হবে। কোন বিপদের ফলে যদি ফসলের কোন ক্ষতি হয়, তাহলে সে ক্ষতিতেও দুই পক্ষ সমান হারে শরীক থাকবে। কিন্তু এক পক্ষের পাওনা যদি নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়, তাহলে সে তো ক্ষতি থেকে বেঁচে যাবে; কিন্তু অপর পক্ষের অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে পড়ে যাওয়া একান্তই অবধারিত। তার ভাগে ঘাস শুকানো ছাড়া আর কিছু মিলবে না। এটা তো সুদ ও জুয়ার সাথে পুরোমাত্রায় সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যাপার। এ দুয়ের মধ্যে মৌলিক কোন পার্থক্য থাকে না।
এ দৃষ্টিতে যখন নগদ টাকায় জমি লাগানোর ব্যাপারটা বিবেচনা করা যায়, তাহলে তাতেও উপরি উল্লিখিত নিষিদ্ধ ধরনের পারস্পরিক চাষের মধ্যে কোন পার্থক্যই ধরা পড়ে না। জমি মালিক নগদে তার পাওনাটা নিশ্চিত রূপেই পেয়ে যায়। কিন্তু যে লোক এ টাকা দিয়ে চাষের জন্যে জমি নিল, সে তো নিজের শ্রম, যায়। কিন্তু যে লোক এ টাকা দিয়ে চাষের জন্যে জমি নিল, সে তো নিজের শ্রম, মেহনত ও মূলধন সবকিছুই কঠিন ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দেয়। সে জমি থেকে কিছু পাবে কি না, তার কোন নিশ্চয়তাই তার থাকে না। তাতে ফসল ফলবে কি না, তার কিছুই জানা নেই।
খ. উপরন্তু একজন যখন কোন জিনিস কেরায়ার ভিত্তিতে কাউকে দেয় সে তো তার মালিক। সে তার কেরায়া পাওয়ার অধিকারী হয় এ কারণে যে, সেই জিনিসটিকে ব্যবহার করে ফায়দা লাভের উপযুক্ত করে কেরায়ায় গ্রহণকারীর হাতে সোপর্দ করে দেয়। তা ব্যবহার করার দরুন তাতে যে অপচয় (Depercition) দেখা দেয় তার বিনিময় মূল্য পাওয়ার তার অধিকার রয়েছে। কিন্তু জমিকে কেরায়ায় লাগাতে কোনরূপ প্রস্তুতির প্রয়োজন হয় না। জমিতে উৎপাদন শক্তি তো জমি মালিক সৃষ্টি করেন না, তা তো সম্পূর্ণ আল্লাহরই দান। দ্বিতীয়, চাষাবাদ করা হলে জমির কোন ‘অপচয়’ হয় না, যন্ত্রপাতির ন্যায় তাতে ময়লাও ধরে না, দালান-কোঠার ন্যায় তা পুরাতনও হয়ে যায় না।
গ. এও সত্য যে, কেউ যখন কোন বাড়ি কেরায়ায় গ্রহণ করে, তখন সে তাতে অবস্থান ও বসবাস করে, তা থেকে সরাসরি উপকৃত হয়। মাঝখানে কোন প্রতিবন্ধকতা থাকে না। এমনিভাবে কোন যন্ত্র ভারা করলেও ঠিক সেই আসল জিনিসটার দ্বারাই উপকৃত হওয়া যায়। কিন্তু জমি থেকে সরাসরি উপকার পাওয়া সম্ভব হয় না, আর তা থেকে উপকার লাভ নিশ্চিতও কিছু নয়। জমির ব্যাপারটা ভাড়াটে বাড়ির মতো নয়, তা থেকে ফায়দা লাভ এক অনিশ্চিত ব্যাপার। বরং জমি যখন কেরায়ায় গ্রহণ করে কেউ, তখন সে তা থেকে উপকৃত হওয়ার আশাতেই করে। আর এ আশায়ই সে তাতে শ্রম মেহনত করে, পয়সা ও সময় ব্যয় করে, তারপরও সে তা থেকে কখনও ফায়দা লাভ করে, কখনও তা করে না। কাজেই জমি ভাড়ায় গ্রহণকে বাড়ি ইত্যাদি কেরায়ায় লওয়ার মতো মনে করা ঠিক নয়।
ঘ. সহীহ্ হাদীসে উদ্ধৃত হয়েছেঃ
ফল-ফলাদি পরিপক্ক হওয়ার পূর্বে ক্ষেতে ও বাগানে থাকা অবস্থায় ক্রয়-বিক্রয় করতে নবী করীম (সা) নিষেধ করেছেন। আর তার কারণ স্বরূপ বলেছেন, ‘তোমরা কি ভেবে দেখেছ, আল্লাহ্ যদি ফল থেকে বঞ্চিত করে দেন, তাহলে তোমার ভাইয়ের কাছ থেকে নেয়া টাকা তোমার জন্যে হালাল হতে পরবে কেমন করে? ফলগুলো পাকতে শুরু করেছে, কিন্তু এখনও তা সুরক্ষিতভাবে পেয়ে যাওয়ার কোন নিশ্চয়তা নেই। কেননা তা কোন বিপদের কারণে নাও পাকতে পারে- এই যখন অবস্থা, তখন খালি জমি- যাতে কোদাল পর্যন্ত লাগান হয়নি, তাতে বীজও ফেলা হয়নি- কেরায়ায় দেয়া নিষিদ্ধ হবে না কেন? আসলে সঠিক ও ইনসাফপূর্ণ পন্থা হচ্ছে ফসলের হার ভাগের ভিত্তিতে পারস্পরিক চাষাবাদ। তাতে কাজের উভয় পক্ষই মুনাফা বা ফায়দায় সমানভাবে শরীক থাকে, ক্ষতি হলেও তা দুজনেরই ভাগে পড়ে।
( আরবি******************)
ইমাম ইবনে তাইমিয়া বলেছেন, ফসলের হার ভাগের ভিত্তিতে জমি চাষ করানোই হচ্ছে ইসলামী শরীয়তের মৌলনীতি ও সুবিচার ব্যবস্থার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ পন্থা। আর কেরায়ায় দেয়ার তুলনায় ফসল ভাগের ভিত্তিতে চুক্তি অধিকতর সুবিচার ও ন্যায়পরতা সম্পন্ন। কেননা এ পন্থাতেই উভয় পক্ষ লাভ ও লোকসান উভয়তেই শরীক থাকে। জমি কেরায়ায় দেয়ার ব্যাপারটি ভিন্নতর। তাতে জমি-মালিক কেরায়া তো পেয়ে যায়, কিন্তু কেরায়াদারের ভাগে কখনও ফসল উঠে আর কখনও তাকে তা থেকে বঞ্ছিত থাকতে হয়।
( আরবি******************)
ইমাম ইবনুল কাইয়্যেম লিখেছেনঃ
যে ধরনের পারস্পরিক চাষাবাদ ইনসাফপূর্ণ, মুসলমানরা তদানুযায়ী রাসূলে করীম (সা) ও খুলাফায়ে রাশেদুনের আমল থেকেই কাজ করে আসছে। আবূ বকর-উমর- উসমান-আলী (রা)-এর বংশধররাও তাই করেছেন। বড় বড় সাহাবী সাটাকেই জায়েয মনে করতেন। হযরত ইবনে মাসউদ, উবাই ইবনে কা’ব, যায়দ ইবনে সাবিত প্রমূখ সাহাবী (রা) এ মতই পোষণ করতেন। মুহাদ্দিস-ফিকাহবিদ ইমাম আহমেদ ইবনে হাম্বল, ইসহাক ইবনে বাহওয়াই, ইমাম বুখারী, দাঊদ ইবনে আলী, ইবনে খুজাইমা, আবূ বকর ইবনুল মুনযির, মুহাম্মদ ইবনে নছর মরোজী প্রমুখও এ মতকেই যথার্থ ঘোষণা করেছে। আর মুসলমানদের নামকরা ফিকাহবিদ লাইস ইবনে সা’দ ইবনে আবূ রাইলা, আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মাদ ইবনে ইমাম হাসান প্রমুখও এ মতই প্রকাশ করেছেন।
ইবনুল কাইয়্যেমের সময়ে কৃষিজীবীদের ওপর প্রশাসক ও সেনাবাহিনীর লোকদের পক্ষ থেকে যে জোর-জুলুম চালান হয়েছে, তিনি তার তীব্র প্রতিবাদ করেছেন। তিনি বলেছেনঃ এ প্রশাসক ও সৈন্যবাহিনীর লোকেরা যদি আল্লাহ্ ও রাসূলের দেয়া শরীয়তের বিধান অনুযায়ী চাষীদের সাথে ব্যবহার করত, তাহলে তারা সকলে উপর ও নিচ থেকে দেয়া আল্লাহর অফুরন্ত নিয়ামত লাভ করতে পারত। আসমান ও জমিনের বরকতের দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়া হতো। তারা জুলুম ও নির্যাতন করে যা পায়, এক-চতুর্থাংশ গ্রহণ করলে তাও তার চাইতে অনেক বেশি হতো। কিন্তু ওরা মূর্খ, ওরা জালিম। তাই জুলুম ও পাপ ভিন্ন ওদের করার আর কিছুই নেই। ফলে ওরা বরকত ও রিযকের প্রশস্ততা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। আর তার দরুন তাদের জন্যে পরকালীন আযাবই পুঞ্জীভূত হয়ে থাকল। দুনিয়ার কোন বরকত তাদের ভাগ্যে জুটবে না।
যদি প্রশ্ন করা হয়, আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল এ পর্যায়ে কি বিধান দিয়েছেন এবং সাহাবিগণই বা কোন্ নীতি মেনে চলেছেন?
উত্তরে বলা যাবে, ঠিক যে পন্থা পারস্পরিক ইনসাফপূর্ণ, যাতে জমি মালিক ও চাষী সুবিচারের এক ও অভিন্ন মানে উত্তীর্ণ হতে পারে, প্রচলিত নিয়মে যেমন হয় তেমন বিশেষ এক পক্ষকে তার ভাগ্য সম্পর্কে নিশ্চয়তা দেয়ে অপর পক্ষকে অনিশ্চয়তার ঝুঁকির মধ্যে নিক্ষেপ করা হয় না, তা-ই। দুনিয়ায় সাধারণভাবে প্রচলিত রসম-রেওয়াজ ভুইফোঁড় নীতিতে চলছে। তা-ই যত বিপর্যয় এনেছে পৃথিবীতে। জনগণকেও নিক্ষেপ করেছে কঠিন সংকটের মধ্যে। বৃষ্টি পড়া বন্ধ হয়েছে, বরকত উঠে গেছে। প্রশাসন ও সেনাবাহিনীর অধিকাংশ লোক হারাম খেতে শুরু করেছে। আর হারাম খাদ্যে তাদের দেহে যে গোশত জমেছে, তার জন্যে তো জাহান্নামই উপযুক্ত স্থান।
এই ইনসাফপূর্ণ কৃষি ব্যবস্থাই ছিল মুসলিম জনগণের অনুসৃত নীতি। নবী করীম (সা)-এর যুগেও যেমন, তেমন খুলাফায়ে রাশেদুন ও তৎপরবর্তীকালেও। স্বয়ং নবী করীম (সা) খায়বরবাসীদের সাথে এ নীতির ভিত্তিতেই জমি চাষের চুক্তি করেছিলেন। হযরত উমর (রা) তাদের নির্বাসিত না করা পর্যন্ত তদানুযায়ী কাজ হয়েছে। তাতে কথা ছিল তারই জমি চাষাবাদ করবে নিজেদের খরচ, বীজও তারাই দেবে।
এ কারণে আলিমদের মতে বীজ চাষির দেয়া উচিত হলেও দুজনের যে কোন একজন দিলেও জায়েয হবে। হযরত উমর (রা) এভাবে চুক্তি করেছিলেন যে, তিনি বীজ দিলে অর্ধেক ফসল পাবেন। আর চাষকারী যদি তা দেয়, তবে সেও তাই পাবে অর্থাৎ অর্ধেকেরও বেশি।
পারস্পরিক জমি চাষ পর্যায়ে যত হাদীসের বর্ণনাই পাওয়া যায়, তাতে চাষকারী যে অর্ধেকের কম পাবে, তার কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না; বরং তারও বেশি পাওয়ার কথা কোন কোন বর্ণনায় বলা হয়েছে।
এ প্রেক্ষিতে মন বলছে, চাষকারীর অংশ অর্ধেকের কম হওয়া উচিত নয়। নবী করীম (সা) ও খুলাফায়ে রাশেদুন খায়বারের ইয়াহূদীদের সাথে তাই করেছেন। অতএব ফসল বন্টনের সময় মানুষের (চাষকারীর) অংশের তুলনায় পাথরের- জমির- অংশ বেশি হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।
পশুপালনে শরীকানা
আমাদের দেশে বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে আর একটা কাজের প্রচলন রয়েছে তা হচ্ছে পশু-জন্তু পালনে শরীকী ব্যবস্থা। এক পক্ষ সম্পূর্ণ বা কতক মূলধন দেয় আর অপর পক্ষ দেখা-শোনার দায়িত্ব পালন করে। আর ফল বা মুনাফা দুজনে ভাগ করে নেয়।
এ সম্পর্কে শরীয়তের রায় জানার পূর্বে এ কাজের বিভিন্ন ধরন বিশ্লেষণ করা আবশ্যক।
১. একটি ধরন এই যে, নিছক ব্যবসায়ী উদ্দেশ্যে উভয় পক্ষ একত্রিত হবে। বাছুর মোটা করার উদ্দেশ্যে পালন বা গাভী-মহিষ থেকে দুগ্ধ লাভের উদ্দেশ্যে পালন।
এতে এক পক্ষ মূলধন দেয় আর অপর পক্ষ দেয় শ্রম ও দেখা-শোনার কাজের দায়িত্ব। পশুগুলোর খাদ্য পানীয় দিতে যা ব্যয় হবে তা দুজনই বহন করবে। আর তা বিক্রয় করা হলে যে মূল্য পাওয়া যাবে, তা থেকে খরচ বাদ দেয়া হবে। তার পরে যা মুনাফা দাঁড়াবে তা দুজনে নিজেদের মধ্যে চুক্তি অনুযায়ী বন্টন করে নেবে।
যদি এক পক্ষই সমস্ত খরচ বহনে বাধ্য হয়, আর তার বিনিময়ে সে কিছু না পায়, অথচ মুনাফা দুজনের মধ্যে সমান হারে ভাগ করা হয়, তবে তা ইনসাফপূর্ণ ব্যবসা হতে পারল না।
২. দ্বিতীয় ধরন এই হয় যে, এক পক্ষ মূল্য দেবে আর অপর পক্ষ খরচ ও দেখাশোনার দায়িত্ব বহন করবে। আর জন্তুর দুগ্ধ নিয়ে কিংবা চাষাবাদ বা পানি বহনের কাজে সে পশু ব্যবহার করে উপকৃত হবে।
হ্যাঁ, এরূপ করায় কোন দোষ নেই, যদি জন্তু আকারে বড় হয়, তার থেকে দুধ পাওয়া যায় কিংবা তার দ্বারা কাজ করানো যায়। একথা ঠিক যে, দ্বিতীয় পক্ষ যে খরচ পত্র বহন করে, তার সে সব ব্যয় বহনের তুলনায় দুগ্ধ ইত্যাদি পাওয়াটা সমান মনে হয় না, তাতে ক্ষতির আশংকাটাও থাকে, কিন্তু আমরা ভাল মনে করেই তা জায়েয বলেছি এবং ক্ষতির এ সামান্য আশংকাকে তেমন গুরুত্ব দিই নি। কেননা শরীয়ত এ ধরনের জিনিস সহ্য করে নিতে অসুবিধাবোধ করে না। রাসূলে করীম (সা) বলেছেনঃ ( আরবি******************)
বন্ধকী বাবদ রাখা জন্তুর খরচাদি বহনের বিনিময়ে তাতে সওয়ার হওয়া যায় এবং তার দুগ্ধও পান করা যেতে পারে। সওয়ারী যে করে ও দুগ্ধ যে পান করে খরচাদি তাকেই বহন করতে হবে। (বুখারী)
এ হাদীসে নবী করীম (সা) জন্তুর খাদ্য ইত্যাদি বাবদ খরচের সমান বিনিময় ধরেছেন সেটিকে সওয়ারী রূপে ব্যবহার করা ও সেটির দুগ্ধ পান করাকে।
জন্তুর জন্যে খরচাদি তার ওপর সওয়ার হওয়ার ও তার দুগ্ধ পান করার তুলনায় অনেক বেশি হতে পারে, কমও হতে পারে। কিন্তু প্রচলনের দৃষ্টিতে যখন বন্ধকীর ক্ষেত্রে এ অবস্থাকে জায়েয মনে করা হয়েছে তখন জন্তু পালনের আলোচ্য শরীকী ব্যবসাকেও প্রয়োজনের দৃষ্টিতে জায়েয মনে করতে কোনরূপ দ্বিধা বোধ হয় না।
উপরিউদ্ধৃত হাদীস থেকে যে প্রতিপাদ্য আমরা বের করেছি তা একান্তভাবে এ গ্রন্থকারের মত। আল্লাহ্ এ মতটিকে নির্ভুল করুন।
কিন্তু ছোট বাছুর জাতীয় জন্তু পালনে- যাতে তার ওপর সওয়ার হওয়াও যায় না, তার দুগ্ধও পান করা যায় না- যদি এক পক্ষ মূল্য দেয় আর অপর পক্ষ খরচাদি বহন করে, তাহলে তা ইসলামের মৌলনীতির দৃষ্টিতে মুবাহ মনে করা যায় না। কেননা যে পক্ষকে খরচাদি বহন করতে হবে সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আর অপর পক্ষ কেবল সুবিধা ও লাভই লাভ পাবে। অতএব তা যেমন ন্যায়ভিত্তিক নয়, তা সুস্পষ্ট অথচ ইসলাম সর্ব ব্যাপারে ইনসাফ ও ন্যায়পরতাকে কার্যকর দেখতে চায়। তবে খরচাদি বহনকারী পক্ষের ফায়দা পাওয়ার সময় হওয়া পর্যন্ত সমস্ত খরচ যদি উভয় পক্ষ পারস্পরিক বন্টনের মাধ্যমে বহন করে, তাহলে আমরা মনে করি, তা জায়েয হবে।
ক্রীড়া ও আনন্দ
ইসলাম বাস্তববাদী জীবন-বিধান। তা মানুষকে অবাস্তব কল্পনা বিলাস ও নানা চিন্তা ভাবনার কুঙঝটিকার পরিবেষ্টনে আবদ্ধ করে রাখতে ইচ্ছুক নয়। বরং এ বাস্তবতার পৃথিবীতে ঘটনা প্রবাহের আবর্তনের মধ্যে সুষ্ঠু রূপে বসবাস করার নীতে ও পদ্ধতিই ইসলাম মানুষকে শিক্ষা দেয়। তা মানুষকে নভোমণ্ডলে বিচরণকারী ফেরেশতা মনে করে কর্মবিধান তৈরী করেনি। খাদ্য-পানীয় গ্রহণকারী ও হাটে-বাজারে বিচরণকারী মানুষ মনে করেই তার জন্য বিধান দেয়া হয়েছে।
এ কারণে মানুষের প্রতিটি কথা ‘যিকির’ হবে, চুপ করে থাকলেও গভীর গবেষণায় নিমজ্জিত হতে হবে, কেবলমাত্র কুরআনের ধ্বনিই তাদের কর্ণ-কুহরে প্রবেশ করবে, সমস্ত অবসর কাল অতিবাহিত হবে মুসজিদে- এমন কথা কল্পনা করা যায় না, তার আশাও করা যায় না এবং ইসলাম মানুষের ওপর এ কর্তব্য চাপয়েও দেয়নি, এ বাধ্যবাধকতাও আরোপ করেনি। সত্যি কথা হচ্ছে, ইসলাম মানুষের প্রকৃতি ও স্বভাবগত ভাবধারার ওপর পুরো মাত্রায় লক্ষ্য নিবদ্ধ রেখেছে। আল্লাহ্ তা’আলা মানুষকে সৃষ্টিই করেছেন এভাবে যে, পানাহার যেমন তার প্রকৃতির চাহিদা তেমনি আনন্দ-স্ফূর্তি ও সন্তুষ্ট-উৎফুল্লচিত্ত হয়ে থাকা এবং হাসি-তামাসা-খেলা ইত্যাদিও তার প্রকৃতিগত ভাবধারা হয়ে রয়েছে। এ সত্য কোন ক্রমেই অস্বীকার করা যায় না।
প্রতি মুহূর্তে একই অবস্থা থাকে না
কোন কোন সাহাবী আধ্যাত্মিকতার প্রাধান্য ও তাতে সর্বোচ্চ উন্নতি লাভের ফলে মনে করতে শুরু করেছিলেন যে, সব সময় ইবাদতের মধ্যে ডুবে থাকাই তাদের কর্তব্য এবং বৈষয়িক স্বার্থ স্বাদ-আনন্দ পরিহার করে চলাই বাঞ্ছনীয়। ক্রীড়া আনন্দ স্ফূর্তিতে তাদের অংশ গ্রহণ করা উচিত নয়। সম্পূর্ণভাবে পরকালমুখী ও পরকালীন ধ্যান-ধারণা ও দায়-দায়িত্ব পরিপূরণে আত্মসমর্পিত হয়ে থাকা একান্তই আবশ্যক।
এ পর্যায়ে মহামান্য সাহাবী হযরত হিনজিলা উসাইদী (রা)-এর একটি কাহিনী উল্লেখ্য। তিনি রাসূলে করীম (সা)-এর বিশেষভাবে নিয়োগকৃত একজন লেখক ছিলেন। তিনি নিজের সম্পর্কে নিজেই বলেছেনঃ
হযরত আবূ বকর (রা) আমার সাথে সাক্ষাত করলেন। জিজ্ঞেস করলেনঃ কি অবস্থা হে হিনজিলা? বললামঃ হিনজিলা তো মুনাফিক হয়ে গেছে। তিনি বললেনঃ সুবহান-আল্লাহ্ বল কি? তখন আমি বললামঃ হ্যা, ব্যাপার তো তা-ই। আমরা যখন রাসূলে করীম (সা)-এর দরবারে বসা থাকি ও তিনি জান্নাত ও দোযখের কথা স্মরণ করিয়ে দেন, তখন অবস্থা এমন হয়, যেন আমরা তা নিজেদের চোখে প্রত্যক্ষ করছি। কিন্তু যখন সেই দরবারের বাইরে চলে আসি, তখন স্ত্রী-পুত্র-পরিজন ও কায়কারবারে মন লাগিয়ে দিই; জান্নাত ও দোযখের কথা তখন অনেক খানিই ভুলে যাই। একথা শুনে হযরত আবূ বকরও বললেনঃ আল্লাহর নামে শপথ! আমার অবস্থাও তো ঠিক তদ্রুপ। হিনজিলা বলেনঃ অতঃপর আমরা দুজন- আমি ও আবূ বকর নবী করীমের খেদমতে উপস্থিত হলাম এবং বললামঃ ইয়া রাসূল! হিনজিলা তো মুনাফিক হয়ে গেছে! রাসূলে করীম (সা) বললেনঃ সে কি রকম? আমি বললামঃ ইয়া রাসূল! আমরা যখন আপনার কাছে থাকি, আপনি জান্নাত জাহান্নামের কথা বলেন, তখন আমরা তা যেন স্পষ্ট দেখতে পাই- এমন অবস্থা হয়। কিন্তু এখান থেকে যখন বের হয়ে যাই, তখন আমরা স্ত্রী-পুত্র-পরিজন ও কায়কারবার নিয়ে এত মশগুল হয়ে যাই যে, অনেক কিছুই আমরা ভুলে যাই।
এসব কথা শুনে নবী করীম (সা) ইরশাদ করলেনঃ ( আরবি******************)
যাঁর হাতে আমার জীবন তাঁর নামে শপথ, তোমরা আমার কাছে এবং যিকিরের মধ্যে যে অবস্থা ও ভাবধারা অনুভব কর, তার মধ্যে যদি তোমরা সব সময়ই থাকতে তাহলে ফেরেশতাগণ এসে তোমাদের বিছানায় ও পথেঘাটেই তোমাদের সাথে করমর্দন করত। কিন্তু হে হিনজিলা! সময়ে সময়ে পার্থক্য রয়েছে। সব সময় এক অবস্থায় থাকা যায় না- এই কথাটি তিনি পরপর তিনবার বললেন। (মুসলিম)
রাসূল তো মানুষ ছিলেন
রাসূলে করীম (সা) মানুষ ছিলেন এবং তাঁর উন্নত জীবন পূর্ণাঙ্গ ও সর্বোন্নত মানের মানব জীবনের জন্যে উজ্জ্বল ভাস্বর আদর্শ এবং অনুসরণীয়। তিনি নিবিড় একাকীত্বে নামায পড়তেন, দীর্ঘক্ষণ বিনয়-ভীতি, কান্নাকাটি করতেন। দীর্ঘ সময় ধরে দাঁড়িয়ে নামায পড়তেন বলে তাঁর পা দুখানি ফুলে উঠত। তিনি তো পুরোপুরি সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, আল্লাহর দিক দিয়ে তাঁর এক বিন্দু ভয় ছিল না কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি মানবীয় জীবনই যাপন করছিলেন। আর সাধারণ মানুষের ন্যায় তিনি ভাল ও সুঘ্রাণ পছন্দ করতেন, হাসতেন, ঠাট্টা-মশকরা-রসিকতা করতেন, তা তাঁর মহান প্রকৃতির বিশেষত্ব ছিল। কিন্তু তিনি সত্য বিরোধী কথা কখনই বলতেন না।
নবী করীম (সা) আনন্দ-স্ফূর্তি ও হাসি-খুশী থাকা খুব পছন্দ করতেন, কষ্ট ও দুঃখ অপছন্দ করতেন। তিনি সব খারাবী থেকে আল্লাহর কাছে পানা চাইতেন। বলতেনঃ ( আরবি******************)
হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে পানা চাই দুশ্চিন্তা ও দুঃখানুভূতি থেকে।
তিনি ঠাট্টা-মশকরাও করতেন। এক বৃদ্ধা তাঁর কাছে উপস্থিত হয়ে বললঃ হে রাসূল! আপনি আল্লাহর কাছে দো’আ করুন- তিনি যেন আমাকে বেহেশতে দাখিল করেন। তখন নবী করীম (সা) বললেনঃ হে অমুকের মা, ব্যাপার হচ্ছে এই যে, বুড়া-বুড়ি লোক তো বেহেশতে যাবে না। একথা শুনে বৃদ্ধাটি কেঁপে উঠল ও কাঁদতে শুরু করে দিল। সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না মনে করে একেবারে ভেঙ্গে পড়ল। নবী করীম (সা) বৃদ্ধার এ অবস্থা দেখে ব্যাখ্যা করে বললেন যে, এর অর্থ হচ্ছে বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা এ অবস্থায় বেহেশতে যাবে না। বরং আল্লাহ্ তাদের এক নবতর সৃষ্টিতে ধন্য করবেন এবং যৌবনদীপ্ত অবস্থায় তারা বেহেশতে প্রবেশ করবে। তিনি তখন এই আয়াতটি পাঠ করে শোনালেনঃ ( আরবি******************)
আমরা তাদের, বিশেষভাবে নতুনতর সৃষ্টিদান করব, তাদের কুমারী বানিয়ে দেব। তারা নিজেদের স্বামীদের প্রেমিকা ও সমবয়স্ক হবে। (সূরা আল-ওয়াকীয়াঃ ৩৫-৩৮)
মন ক্লান্ত হয়ে পড়ে
নবী করীমের পবিত্র হৃদয় ও মহান চরিত্রবান সাহাবিগণও হাসি-ঠাট্টা-মশকরা করতেন। খেলা-তামাসায় যোগ দিতেন। তাঁরা নিজেদের অন্তর্নিহিত প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতেন। মনকে আনন্দ দান করতেন, হৃদয়ে প্রশান্তি ও সুখানুভূতির ব্যবস্থা অবলম্বন করতেন এবং তার মাধ্যমে নবতর উদ্যম ও কর্মক্ষমতা তৎপরতা লাভ করে নতুন ও তাজা হয়ে কর্মে ঝাঁপিয়ে পড়তেন।
হযরত আলী (রা) বলেছেনঃ ( আরবি******************)
দেহের ন্যায় মনও ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে পড়ে। কাজেই এই ক্লান্তি-শ্রান্তি বিদূরণের জন্যে আশ্চর্য ও বুদ্ধিমানের কথাবার্তা বল।
তিনি আরও বলেছেনঃ ( আরবি******************)
হৃদয়কে সময় অবসর মতো শান্তি সুখ-আনন্দ দান কর। কেননা হৃদয়ে অস্বস্তি তাকে অন্ধ বানিয়ে দেয়।
হযরত আবুদদারদা (রা) বলেছেনঃ ( আরবি******************)
আমি আমার মনকে বাতিলের সাথে কতকটা হাসি-মশকরা করার সুযোগ দিই, যেন তার দরুন সত্যের দুস্কর পথে চলার ব্যাপারে আমার সাহায্য হয়।
অতএব হাসি মশকরার কথাবার্তা বলায় হৃদয়ে যদি হালকা ভাব অর্জিত হয় তাহলে তাতে কোন দোষ নেই। মুবাহ্ ক্রীয়া খেলা দ্বারা যদি নিজের মন ও সঙ্গী-সাথীদের সান্তনা-প্রশান্তি লাভের ব্যবস্থা করা হয়, তাতেও কোন গুনাহ হবে না, যদি তা স্থায়ী অভ্যাসে পরিণত হয়ে না পড়ে এবং সর্বক্ষণ কেবল তাতেই মগ্ন থাকার প্রবণতা সৃষ্টি না হয়। কেননা সেরূপ হলে তো সকাল-সন্ধ্যা তাতেই কাটাতে হবে ও তার ফলে দায়িত্বসমূহ পালনে অনীহা দেখা দেবে। এমনকি যেখানে গম্ভীরতা অবলম্বন জরুরী, সেখানেও হাসি-মশকরা শুরু করে দেবে। এ জন্যেই বলা হয়েছেঃ ( আরবি******************)
খাদ্যে যতটা লবণ দেয়ার প্রয়োজন, কথাবার্তায় ঠিক ততটা রসিকতা মিশ্রিত কর।
কেননা লোকদের সম্মান ও ইজ্জত-হুরমতের প্রতি লক্ষ্য না দিয়ে তাদের কেবল বিদ্রুপ করা মুসলমানের কাজ হতে পারে না। এ জন্যে আল্লাহ্ তা’আলা ইরশাদ করেছেনঃ ( আরবি******************)
হে ঈমানদার লোকেরা, লোকেরা যেন পরস্পরে বিদ্রুপ ও অপমানসূচক আচরণ না করে। কেননা হতে পারে সে তার চেয়েও অনেক ভাল। (সূরা হুজরাতঃ১১)
লোকদের হাসাবার উদ্দেশ্যে মিথ্যা কথার আশ্রয় লওয়াও সমীচীন বা জায়েয নয়। এ বিষয়ে সতর্ক করে দিয়ে নবী করীম (সা) বলেছেনঃ ( আরবি******************)
ধ্বংস তার, যে লোকদের হাসাবার জন্য মিথ্যা কথা বলে। তার ধ্বংস, তার জন্যে ধ্বংস। (তিরমিযী)
জায়েয ধরনের খেলা
আনন্দ-স্ফূর্তি ও ক্রীড়ার বহু প্রকার ধরন ও পদ্ধতি এমন রয়েছে যা নবী করীম (সা) মুসলমানদের জন্যে জায়েয ঘোষণা করেছেন। মুসলমানরা এগুলোর সাহায্যে মনের বোঝা হালকা করতে পারে, স্ফূর্তি লাভ করতে পার। এসব ক্রীড়া মানুষকে ইবাদত ও কর্তব্য পালনে- এসব কাজে তৎপরতা সহকারে অংশ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে। এসব শরীর চর্চামূলক ক্রীড়ার সাহায্যে শক্তিবর্ধক ট্রেনিং লাভ করতে পারে। তার দরুন মানুষ জিহাদে অংশ গ্রহণের জন্যেও প্রস্তুত হতে পারে। নিম্নোদ্ধৃত ক্রীড়াসমূহ এ পর্যায়ের খেলাঃ
দৌড় প্রতিযোগিতা
সাহাবায়ে কিরাম দৌড়ে প্রতিযোগিতা করতেন। নবী করীম (সা) তা করার জন্যে তাদের অনুমতি দিয়েছিলেন। হযরত আলী (রা) দৌড় লাগানর কাজে খুব দ্রুত গতিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন বলে বর্ণিত হয়েছে।
স্বয়ং নবী করীম (সা) তাঁর মুহতারিমা বেগম হযরত আয়েশা (রা)-এর সাথে তাকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে এবং সাহাবায়ে কিরাম (রা)-কে শিক্ষা দানের উদ্দেশ্যে দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতেন। হযরত আয়েশা (রা) নিজেই বলেছেনঃ ( আরবি******************)
নবী করীম (সা) দৌড়ে আমার সাথে প্রতিযোগিতা করলেন। তখন আমি আগে বেরিয়ে গেলাম। পরে যখন আমার শরীর ভারী হয়ে গেল তখনও আমার সাথে দৌড় প্রতিযোগিতা করে আমাকে হারিয়ে দিলেন এবং বললেনঃ এবার সেবারের বদলা নিলাম। (আহমদ, আবূ দাঊদ)
কুস্তি করা
নবী করীম (সা) রুকানা নামক এক নামকরা কুস্তিগীরের সাথে লড়েছিলেন। তাতে তিনি একাধিকবার তাকে আছাড় দিয়ে ফেলে দিয়েছিলেন। (আবূ দাঊদ)
অপর এক বর্ণনায় বলা হয়েছেঃ নবী করীম (সা) যাকে ধরাশায়ী করে দিয়েছেন তিনি ছিলেন নিরতিশয় বলিষ্ঠ। তিনি পর পর তিনবার তাকে ধুলিসাত করেন। ফিকাহবিদগণ এ সব হাদীসের ভিত্তিতে মত দিয়েছেন যে, দৌড়ে প্রতিযোগিতা করা সম্পূর্ণ জায়েয, পুরুষরা এক সাথে এ দৌড় দিতে পারে। পুরুষ ও মুহাররম মেয়েরা যৌথভাবে কিংবা স্বামী-স্ত্রীও একত্রে প্রতিযোগিতায় নামতে পারে। দৌড়ে প্রতিযোগিতা ও কুস্তি করা মান-মর্যাদা, গাম্ভীর্য, জ্ঞান-গরিমা ও বয়োবৃদ্ধি কোনটারই পরিপন্থী নয়। কেননা নবী করীম (সা) যখন হযরত আয়েশা (রা)-এর সাথে দৌড়ে প্রতিযোগিতা করেছিলেন, তখন তাঁর বয়স পঞ্চাশোর্ধ হয়েছিল।
তীর নিক্ষেপ
তীরন্দাজী ও বল্লম মারার খেলাও শরীয়াতসম্মত।
নবী করীম (সা) যখন সাহাবায়ে কিরামকে তীর নিক্ষেপণে মশগুল দেখতে পেতেন তখন তিনি তদের সর্বতোভাবে উৎসাহিত করতেন। বলতেনঃ ( আরবি******************)
তোমরা তীর মারো, আমি তোমাদের সঙ্গে রয়েছি।
বস্তুত নবী করীম (সা)-এর দৃষ্টিতে তীর নিক্ষেপণ কেবলমাত্র একটা খেলা ও হাস্য-কৌতুকের ব্যাপারই ছিল না। তা ছিল একটি শক্তি- শক্তি অর্জন ও শক্তি প্রকাশ। আল্লাহ্ তা’আলাই তার নির্দেশ দিয়েছেনঃ
তোমরা শত্রুদের মুকাবিলার জন্য সাধ্যমত শক্তি অর্জন ও সংগ্রহ কর।
এ পর্যায়ে রাসূলে করীম (সা) বলেছেনঃ
জেনে রাখো, তীরন্দাজী একটা শক্তি। তীর নিক্ষেপণ একটা শক্তি, তীর নিক্ষেপণ একটা শক্তি।
তিনি আরও বলেছেনঃ
তীরন্দাজী শিক্ষা লাভ করা তোমাদের কর্তব্য। কেননা তা তোমাদের জন্যে একটা উত্তম খেলাও।
তবে তিনি পালিত জন্তুকে তার লক্ষ্য বানাতে নিষেধ করেছেন। জাহিলিয়াতের যুগে আরবেরা তাই করত। হযরত ইবনে উমর (রা) কতিপয় লোককে তাই করতে দেখে বলেছিলেনঃ
নবী করীম (সা) কোন জীবিত প্রাণবন্ত জিনিসকে তীর নিক্ষেপণের লক্ষ্যরূপে গ্রহণকারীর ওপর অভিশাপ করেছেন।
এ অভিশাপ বর্ষণের কারণ হল, এতে যেমন ধন-সম্পদের অপচয় হয়, তেমনি জীবনে কষ্ট দান করা হয়, নিজেকেও ধ্বংস করা হয়। বস্তুত জগতের কোন জীবন সত্তার ওপর কষ্ট দিয়ে নিজেদের আনন্দ-উৎসব অনুষ্ঠান করাটা মানুষের জন্যে কখনো শোভন হতে পারে না।
ঠিক এ কারণে নবী করীম (সা) জন্তুগুলোকে উত্তেজিত করে দিয়ে পারস্পরিক লড়াইয়ে লিপ্ত করতে স্পষ্ট ভাষায় নিষেধ করেছেন। (আবূ দাঊদ, তিরমিযী)। তদানীন্তন আরবের লোকেরা দুটো ছাগল কিংবা দুটো বলদ (ষাড়)-কে পারস্পরিক লড়াইতে এমনভাবে লিপ্ত করে দিত যে, সে দুটো লড়াই করে করে ধ্বংস ও মৃত্যমুখে পতিত হয়ে যেত। আর তা দেখে তারা উল্লসিত হতো, অট্রহাসিতে ফেটে পড়ত। এ কাজ নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ দর্শাতে গিয়ে বিশেষজ্ঞগণ বলেছেনঃ ( আরবি******************)
এ কাজে জন্তুগুলোকে মর্মান্তিকভাবে পীড়া ও কষ্ট দেয়া হয়। ওদের কঠিন দুরবস্থার মধ্যে ফেলে দেয়া হয়। উপরন্তু তা এক নিষ্ফল কর্ম ছাড়া আর কিছুই নয়।
বল্লম চালানো
তীর নিক্ষেপণের ন্যায় বল্লাম চালানোও এক প্রকারের বৈধ খেলা। নবী করীম (সা) হাবশীদেরকে মসজিদের মধ্যে বল্লম চালানোর খেলা খেলবার অনুমতি দিয়েছিলেন। আর তাঁর স্ত্রী হযরত আয়েশা (রা) কে অনুমতি দিয়েছিলেন ঘরের মধ্যে থেকে তা দেখতে। তিনি তাদের উৎসাহ দানের জন্যে বলছিলেনঃ হে বনী আরফাদা, মারো, জোরে মারো, তোমার কাছেই রয়েছে তোমার প্রতিপক্ষ।
হযরত উমর (রা) কঠোর মেজাযের লোক ছিলেন বলে এ খেলা তাঁর ভাল লাগেনি। তিনি তাদের নিষেধ করতে চেয়েছিলেন কিন্তু নবী (সা) তাঁকে বিরত রাখলেন। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেছেনঃ হাবশীরা নবী করীম (সা) এর সম্মুখেই বল্লম দিয়ে খেলছিল। এ সময় হযরত উমর উপস্থিত হলেন। তিনি এ খেলা থেকে ওদের বিরত রাখার ও নিষেধ করার উদ্দেশ্যে ওদের প্রতি পাথর কুচি নিক্ষেপ করলেন। নবী করীম (সা) বললেনঃ ওদের খেলতে দাও হে উমর।
নবী করীম (সা) তার পবিত্র মসজিদের মধ্যে এ খেলা খেলবার অনুমতি দিয়ে বিরাট উদারাতা ও সহনশীলতার পরিচয় দিয়েছিলেন। এর ফলেই মসজিদে দ্বীন ও দুনিয়া উভয়ই একত্রিত ও সমন্বিত হয়েছিল। যেন মুসলমানরা যখন খেলা করে, হাস্যরস করে তখন যেন মনে করে যে, এটা নিছক খেলাই নয়। এটা যেমন খেলা- চিত্ত বিনোদনের মাধ্যম, তেমনি তা শরীর চর্চা ও ব্যায়াম অনুশীলনও বটে! এ হাদীসের আলোকে বিশেষজ্ঞগণ মত দিয়েছেন যেঃ ( আরবি*******************)
মসজিদ হচ্ছে মুসলিম সমাজের যাবতিয় কাজের কেন্দ্রস্থান। কাজেই যে যে কাজে দ্বীন ও দ্বীনদার লোকদের কল্যাণ নিহিত, তা তাতে করা নিঃসন্দেহে জায়েয।
এ প্রেক্ষিতে এ কালের মুসলমানদের ভেবে দেখা উচিত, তাদের মসজিদসমূহকে সে কালে কিভাবে জীবন ও শক্তির উৎস বানান হয়েছিল। আর বর্তমানে তো তা অকর্মাদের আলস্য কেন্দ্র বানিয়ে রাখা হয়েছে। তাতে না জীবনের স্পন্দন পাওয়া যায় , না কোন শক্তি লাভের উপায় আছে তা থেকে। উপরন্তু স্ত্রীদের সাথে সম্পর্ক রক্ষা ও মুয়ামিলাকরণ এবং এ ধরনের মুবাহ খেলা- তামাসার সাহায্যে মন-অন্তরকে উৎফুল্লকরণ পর্যায়ে রাসূলে করীমের পথ-নির্দেশও এ থেকে পাওয়া যায়। নবী করীমের বেগম আয়েশা (রা) বলেছেনঃ ( আরবি*******************)
আমি দেখছিলাম, রাসূলে করীম (সা) তাঁর চাদর দ্বারা আমাকে আবৃত করছিলেন। আর আমি হাবশীদের দেখছিলাম তারা মসজিদে খেলা করছিল। দেখতে দেখতে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়লাম। অতএব তোমরা খেলায় উৎসাহী ছোট বয়সের বালিকাদের খেলায় নিয়োজিত করতে পার। (বুখারী, মুসালিম)
তিনি আরও বলেছেনঃ আমি রাসূলে করীমের সামনে তাঁর ঘরে মেয়েদের সঙ্গে খেলতাম। আমার কতিপয় বান্ধবী ছিল, তারা আমার সাথে খেলত। রাসূলে করীম (সা) ঘরে এলেই ওরা আত্মগোপন করে বসত। তখন নবী করীম (সা) আমার সঙ্গে ওদের নিয়ে তামাসা করতেন। ফলে ওরা আমার সাথে খেলতে সাহস পেত। (বুখারী, মুসলিম)
ঘোড় সাওয়ারী
আল্লাহ্ তা’আলা ইরশাদ করেছেনঃ ( আরবি*******************)
ঘোড়া, খচ্চর, গাঁধা তোমাদের সওয়ারীর জন্যে বানিয়েছি এরং তা তোমাদের সৌন্দর্য বৃদ্বিকারকও। (সূরা নহলঃ ৮)
রাসূলে করীম (সা) বলেছেনঃ ( আরবি*******************)
ঘোড়াগুলোর ললাট কল্যাণে আবদ্ধ। (বুখারী)
তিনি আরও বলেছেনঃ তীর চালাও, ঘোড়া-সওয়ারী কর।
যে কাজে আল্লাহর যিকির নেই, তা নিতান্তই খেলা এবং নিরর্থক। চারটি কাজ তার ব্যতিক্রম। তা হচ্ছে, দুই লক্ষস্থলের মাঝে দৌড়ানো, ঘোড়া প্রশিক্ষণ, নিজ স্ত্রী-পরিজনের সাথে খেলা করা ও সাঁতার কাটা শেখানো। হযরত উমর (রা) বলেছেনঃ ( আরবি*******************)
তোমাদের সন্তানদের সাঁতার কাটা ও তীর নিক্ষেপণ শিক্ষা দাও। ঘোড়ার পীঠে লস্ফ দিয়ে উঠে শক্ত হয়ে বসতেও তাদের অভ্যস্ত কর। (মুসলিম)
হযরত ইবনে উমর (রা) বলেছেনঃ নবী করীম (সা) ঘোড়ার দৌড় প্রতিযোগিতা করিয়েছেন। যেটি জিতেছে সেটিকে পুরস্কারও দিয়েছেন।
এ সব হচ্ছে দৌড় প্রতিযোগিতার সর্বাগ্রে চলে যাওয়ার জন্যে রাসূলে করীমের উৎসাহ দান পর্যায়ের কাজকর্ম। তা যেমন খেলা, তেমনি চর্চা এবং ব্যায়ামও।
হযরত আনাস (রা)-কে জিজ্ঞেসা করা হলো, আপনার কি রাসূলে করীমের সময়ে বাজি ধরতেন? বললেন, হ্যা। তিনি নিজে ‘সারহা’ নামক ঘোড়ার ওপর বাজি ধরেছিলেন। সেটি সবার আগে চলে গিয়েছিল এবং তা দেখে তিনি খুবই আনন্দিত-উৎসাহিত হয়েছিলেন। ( আরবি*******************)
জায়েয ধরনের বাজি ধরার পদ্ধতি এই যে, তাতে অংশগ্রহণকারী পক্ষদ্বয়ের তরফ থেকে পুরস্কার ঘোষিত হবে না। তা অন্য কারো তরফ থেকে হবে কিংবা হবে মাত্র একটি পক্ষ থেকে। যদি উভয় পক্ষের তরফ থেকে হয়, বলা হয় যে জিতবে সে পুরস্কার পাবে, তাহলে তা জুয়া হবে। আর জুয়া তো নিষিদ্ধ। যেসব ঘোড়া জুয়া খেলায় ব্যবহৃত হয়, রাসূলে করীম তাকে শয়তানী ঘোড়া বলেছেন। তার মূল্য গ্রহণ, তাকে ঘাস খাওয়ান এবং তার পীঠে সওয়ার হওয়াকে গুনাহ বলেছেন। (আহমদ)
তিনি বলেছেনঃ ঘোড়া তিন ধরনের হয়ে থাকে। আল্লাহর ঘোড়া, মানুষের ঘোড়া, শয়তানের ঘোড়া। যে ঘোড়া আল্লাহ্র পথে জিহাদের কাজে নিয়োজিত, তা আল্লাহ্র ঘোড়া। তাকে ঘাস খাওয়ান- তার পায়খানা পেশাব সবকিছুতেই কল্যাণ নিহিত। আর যে ঘোড়া জুয়া খেলায় বা বাজি ধরায় বা রেস খেলায় ব্যবহৃত, তা শয়তানের ঘোড়া! আর লোকেরা যে সব ঘোড়া বংশ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে লালন-পালন করে, তা মানুষের ঘোড়া। তা দারিদ্র্য বিদূরণের কাজে লাগে।
শিকার করা
বড় উপকারী ও কল্যাণময় খেলা হচ্ছে শিকার করা। ইসলাম এ কাজকে খুবই গুরুত্ব দিয়েছে। বস্তুত এ কাজে যেমন সামগ্রী মেলে, উপার্জন হয়, তেমন তা ব্যায়াম চর্চাও বটে। তা কোন যন্ত্রের যেমন তীর বা বল্লমের সাহায্যে হোক কিংবা শিকারী কুকুর বা পাখি দ্বারা হোক, উভয় ধরনের শিকারই জায়েয। এ কাজের জরুরী শর্ত ও নিয়মাদি আমরা ইতিপূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।
ইসলাম মাত্র দুটি সময়ে শিকার করতে নিষেধ করেছে। এ ছাড়া সব সময়ই তা করা যায়। সে দুটি সময় হচ্ছে, হজ্জ ও উমরার জন্যে বাঁধা ইহরাম অবস্থায়। কেননা এ হচ্ছে পরম শান্তি ও পূর্ণাঙ্গ নিরাপত্তার সময়। এ সময় হত্যাও করা যায় না, রক্তপাতও করা যায় না। যেমন আল্লাহ্ নিজেই বলেছেনঃ
হে ঈমানদার লোকেরা! ইহরাম বাঁধা থাকা অবস্থায় তোমরা শিকার হত্যা করো না। আর তোমরা যতক্ষণ ইহরাম বাঁধা অবস্থায় থাকবে ততক্ষণ স্থলভাগের শিকারও হারাম করে দেয়া হয়েছে তোমাদের জন্যে।
আর দ্বিতীয় অবস্থা হচ্ছে মক্কার হারাম শরীফের মধ্যে থাকাকালে। কেননা আল্লাহ্ তা’আলা হারাম শরীফকে সর্বদিক দিয়ে শান্তি ও নিরাপত্তার প্রাণকেন্দ্র বানিয়েছেন। এখানে প্রত্যেকের জন্যেই শান্তি ও নিরাপত্তা। এমনকি কোন জীবন্ত শিকার তথায় আশ্রয় নিলেও এবং তাকে কোন উড়ন্ত পাখি ধরতে পারলেও তা করা যাবে না। নবী করীম (সা) বলেছেনঃ
সেখানকার শিকার শিকার করা যাবে না, সেখানকার গাছ কাটা যাবে না, তার কোন ঘাসও উপড়ান যাবে না।
পাশা খেলা
যে খেলায় জুয়া রয়েছে তা সবই এবং তার প্রতিটিই হারাম। আর যে খেলায় কোন আর্থিক লাভ বা লোকসান হয়ে থাকে, তাই জুয়া। কুরআন মাজীদে মদ্য, স্থানে বলিদান ও তীর দ্বারা ভাগ্য জানতে চাওয়া প্রভৃতি হারাম কাজের সঙ্গে মিলিয়ে এই জুয়ার উল্লেখ করেছে।
নবী করীম (সা) বলেছেন, কেউ যদি বলে যে, এস জুয়া খেলি, তবে তাতে যে গুনাহ্ হবে তার জন্যে তার সদকা করা উচিত। কেননা জুয়া খেলার আহবানটাও একটা পাপ এবং সে পাপের কাফফারা দেয়া বাঞ্ছনীয়।
পাশা খেলা এ পর্যায়েরই একটি খেলা। তার সাথে জুয়া শামিল হলে তা সর্বসম্মতভাবে হারাম। আর কেউ কেউ বলেছেন, মাকরূহ- হারাম নয়। যাঁরা হারাম বলেন, তাঁরা দলিল হিসেবে উল্লেখ করেছেন হযরত বুরায়াদ (রা) বর্ণিত হাদীস। রাসূলে করীম (সা) বলেছেনঃ ( আরবি*******************)
যে লোক পাশা ছক্কা খেলা খেলেছে, সে নিজের হস্ত শূকরের রক্ত-মাংসে রঞ্জিত করেছে।
আবূ মূসা বর্ণিত হাদীস হচ্ছেঃ ( আরবি*******************)
যে লোক পাশা ছক্কা খেলা খেলেছে, সে আল্লাহ্-রাসূলের নাফরমানী করেছে।
এ দুটি হাদীসে স্পষ্ট ভাষায়ই পাশা-ছক্কা খেলা হারাম বলা হয়েছে, তাতে জুয়া থাক, আরি না-ই থাক।
ইমাম শাওকানী লিখেছেনঃ ইবনে মুগফফল ও ইবনুল মুসাইয়্যেবের মতে জুয়া মিশ্রিত না হলে পাশা-ছক্কা খেলায় কোন দোষ নেই। তাঁরা দুজন উপরে উদ্ধৃত হাদীসসমূহকে জুয়া মিশ্রিত পাশা খেলা পর্যায়ের মনে করেছেন।
দাবা খেলা
খুব নামকরা খেলা হচ্ছে দাবা। আরবী ভাষায় বলা হয় শতরঞ্জ। ফিকাহবিদগণ এ খেলা সম্পর্কে বিভিন্ন সিদ্ধান্তে পৌছেছেন। কেউ বলেছেন তা মুবাহ, কেউ বলেছেন মাকরূহ আর কারো মতে তা হারাম।
যাঁরা হারাম বলেছেন, তাঁদের দলিল নবী করীম (সা) থেকে বর্ণিত কতিপয় হাদীস। কিন্তু হাদীস-সনদের সমালোচক ও বিশেষজ্ঞগণ সেসব হাদিসের সত্যতা অস্বীকার করেছে, তাঁরা বলেছেন, এই দাবা খেলা সাহাবীদের জামানাতেই প্রচারিত ও প্রসারিত হয়। তার পূর্বে এই খেলার কোন অস্তিত্ব ছিল না। কাজেই এপর্যায়ে কোন হাদীসের অস্তিত্ব স্বীকৃত নয়। সবই বাতিল। তাহলে এ ব্যাপারে সাহাবীদের কি মত ছিল? জানা যায়, তাঁদের মত এক রকম ছিল না। ইবনে উমর (রা) বলেছেনঃ ( আরবি*******************) ‘দাবা খেলা পাশা-ছক্কা খেলার চাইতেও খারাপ’। হযরত আলী (রা) বলেছেনঃ ( আরবি*******************) এই খেলাও এক প্রকার জুয়াই। কোন কোন সাহাবীর মতে তা মাকরূহ মাত্র।
আবার কোন কোন সাহাবী ও তাবেয়ীর মতে তা মুবাহ, নির্দোষ খেলা। হযরত ইবনে আব্বাস, আবূ হুরায়রা, ইবনে সিরীন, হিশাম ইবনে ওরওয়া, যায়ীদ ইবনুল মুসাইয়্যেব ও যায়ীদ ইবনে জুরাইরা প্রমুখ এ মত প্রকাশ করেছেন।
এ গ্রন্থকারের মতে এ শেষোক্ত মহান বিশেষজ্ঞদের মতই সহীহ। কেননা সত্যি কথা এই যে, এ খেলা হারাম হওয়ার পক্ষে কোন অকাট্র দলিলই পেশ করা যায় নি। তা ছাড়া তাতে যথেষ্ট মানসিক চর্চা ও চিন্তার প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা রয়েছে। এ কারণে এ খেলাকে পাশা ছক্কা থেকে ভিন্নতর মনে করা আবশ্যক। এ করণে তাঁরা বলেছেন যে, পাশা-ছক্কা খেলায় শুধু আনন্দ স্ফূর্তি লাভ হয়। তা-ই তার বৈশিষ্ট্য। কিন্তু শতরঞ্জ বা দাবা খেলার বিশেষত্ব হচ্ছে, তাতে মেধা ও চিন্তাশক্তির প্রাবল্য বিদ্যমান ও প্রয়োজন। কাজেই তাকে তীরন্দাজীর মত মনে করতে হবে।
এই খেলাকে যাঁরা জায়েয বলেছেন, তারা এ পর্যায়ে তিনটি শর্ত আরোপ করেছেনঃ (১) তার কারণে নামাযে যেন বিরম্ব না হয়। কেননা তাতে নামায সময়মত না পড়তে পারার একটা তীব্র আশংকা রয়েছে। (২) তাতে জুয়া থাকতে পারবে না এবং (৩) খেলোয়াড়রা খেলার সময় নিজেদের মুখকে গালাগাল, কুৎসিত-অশ্লীল কথাবার্তা থেকে মুক্ত ও পবিত্র রাখবে। এ সব শর্ত লংঘিত হলে কিংবা তার অংশ বিশেষও ভঙ্গ করা হলে সে খেলাও হারাম হয়ে যাবে।
গান ও বাদ্যযন্ত্র
[এখানে সুযোগ্য গ্রন্থকার বাদ্যযন্ত্র সম্পর্কে সেই হাদীস উল্লেখ করে নি যাতে প্রিয় নবী (সা) ইরশাদ করেছেন, বাদ্যযন্ত্র মিটিয়ে ফেলার জন্যে আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে। বাদ্যযন্ত্র বলতে ঐ সব যন্ত্রকে বোঝায় যা দ্বারা মানুষের সুপ্ত যৌন আকাংখা জাগরিত হয়। -অনুবাদক]
যে কাজে সাধারণতঃ মানুষের মন আকৃষ্ট হয় ও অন্তর পরিতৃপ্তি ও প্রশান্তি লাভ করে এবং কর্ণ কুহরে মধু বর্ষিত হয়, তা হচ্ছে গান বা সঙ্গীত। ইসলামের দৃষ্টিকোণ হচ্ছে, নির্লজ্জতা, কুৎসিত-অশ্লীল ভষা কিংবা পাপ কাজে উৎসাহ উত্তেজনা দানের সংমিশ্রণ না হলে সেই সাথে বাদ্যযন্ত্র ব্যবহারেও কোন দোষ নেই।
আনন্দ উৎসব ক্ষেত্রে খুশী ও সন্তোষ প্রকাশের জন্যে এ সব জিনিস শুধু জায়েযই নয়, পছন্দনীয়ও বটে। যেমন ঈদ, বিয়ে, হারিয়ে যাওয়া আত্মীয়ের ফিরে আসা এবং ওয়ালীমা’র আকীকার অনুষ্ঠান ও সন্তান জন্ম হওয়াকালে এ সব ব্যবহার করা যেতে পারে দ্বিধাহীন চিত্তে।
হযরত আয়েশা (রা) বলেছেন, আনসার বংশের এক ব্যক্তির সাথে একটি মেয়ের বিয়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। তখন নবী করীম (সা) বললেনঃ হে আয়েশা! ওদের সঙ্গে আনন্দ-স্ফূর্তির ব্যবস্থা কিছু নেই? কেননা আনসাররা তো এগুলো বেশ পছন্দ করে। (বুখারী)
হযরত আয়েশা (রা) তাঁর এক নিকটাত্মীয় মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন আনসার বংশের এক ছেলের সাথে। তখন নবী করীম (সা) এসে জিজ্ঞেস করলেন, দুলহিনকে কি পাঠিয়ে দিয়েছ? লোকেরা বলল, জ্বি হ্যাঁ। বললেনঃ তার সাথে একটি গায়িকা মেয়ে পাঠিয়েছ কি? লোকেরা বললঃ জ্বি না। তখন তিনি বললেনঃ
আনসার বংশের লোকেরা খুব গান পছন্দ করে। এ কারণে দুলহিনের সাথে তোমরা যদি এমন একটি মেয়ে পাঠাতে যে গাইতঃ আমরা তোমাদের কাছে এসেছি, আমরা তোমাদের বাড়ি এসেছি, আল্লাহ আমাদেরও বাঁচিয়ে রাখুন, তোমাদেরও, তাহলে খুবই ভাল হতো। (ইবনে মাজা)
হযরত আয়েশা (রা) বলেনঃ তাঁর কাছে উপস্থিত থেকে দুটি মেয়ে ঈদুল-আযাহা’র দিনে গান গাইতেছিল ও বাদ্য বাজাচ্ছিল। নবী করীম (সা) কাপড়মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়েছিলেন। এ সময় হযরত আবূ বকর (রা) তথায় উপস্থিত হলেন। তিনি এ দেখে মেয়ে দুটিকে ধমকালেন। নবী করীম (সা) তা শুনে মুখের কাপড় খুলে বললেনঃ হে আবূ বকর, ওদের করতে দাও। এখন তো ঈদের উৎসব সময়। (বুখারী, মুসলিম)
ইমাম গাজালী তাঁর ‘ইহয়া-উল-উলুম’ গ্রন্থে দুটি মেয়ের গান গাওয়া সংক্রান্ত বহু কয়টি হাদীসের উল্লেখ করেছেন। মসজিদে নববীতে হাবশীদের খেলার ও নবী করীম (সা) কর্তৃক তাদের উৎসাহ দানেরও উল্লেখ করেছেন। নবী করীম (সা) এ সময় হযরত আয়েশাকে জিজ্ঞেস করেছিলেনঃ তুমি কি এ খেলা দেখতে চাও? তার পরে তিনি তাঁর সঙ্গে লেগে থেকে তাকে দেখালেন এবং তাঁর এ সমস্ত হাদীসই বুখারী ও মুসলিম শরীফে উদ্ধৃত হয়েছে। তা অকাট্যভাবে প্রমাণ করে যে, গান ও খেলা সম্পূর্ণ ভাবে হারাম নয়। এ ব্যাপারে শরীয়তের যে রুখছত আছে, তারও প্রমাণ বিদ্যমান।
প্রথমত, খেলার ব্যাপারটি বিবেচ্য। হাবশীদের নৃত্য ও ক্রীড়ামোদিতা সর্বজনবিদিত। দ্বিতীয়ত, তা মসজিদে নববীতে অনুষ্ঠিত হওয়া এবং তৃতীয়ত, রাসূলে করীম (সা) কর্তৃক তাদের বাহবা ও উৎসাহ-উদ্দীপনা দান প্রভৃতিই এসবের মুবাহ হওয়ার প্রমাণ। আর এ সব যখন রয়েছে, তখন তাকে কি করে হারাম বলা যেতে পারে?
চতুর্থ ব্যাপার হচ্ছে, হযরত আবূ বকর ও হযরত উমর তাদের নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু নবী করীম (সা) উভয়কে বারণ করে তা চলতে দিলেন এবং কারণ দর্শালেন এই বলে যে, এটা ঈদ উৎসব। এইটা আনন্দস্ফূর্তি করার সময়। এ গুলোই হচ্ছে আনন্দ-স্ফূর্তি লাভের সামগ্রী।
পঞ্চম কথা, তা দেখার জন্যে নবী করীম (সা)-এর দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করতে থাকা এবং হযরত আয়েশার সাথে আনুকূল্য করতে গিয়ে তাঁর নিজেরও শোনা। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, স্ত্রীলোক ও বাচ্চাদের খেলা দেখিয়ে তাদের আনন্দ দান করা উত্তম চরিত্রসম্পন্ন কাজ। কৃচ্ছ্রতা ও পরহেজগারীর শুস্কতা কঠোরতা গ্রহণ করে তা থেকে বিরত থাকা বা তা করতে না দেয়া- অন্যদের তা থেকে বিরত রাথার তুলনায় এ কাজ অনেক ভাল।
ষষ্ঠ হচ্ছে, তিনি শুরুতেই হযরত আয়েশাকে বললেনঃ
তুমি কি দেখতে চাও?
আর সপ্তম হচ্ছে, দুটো মেয়েকে গান গাইতে ও বাদ্য বাজাতে অনুমতি দান।
বহু সংখ্যক সাহাবী ও তাবেয়ীন গন শুনেছেন এবং তাতে কোন দোষ মনে করেন নি, একথা নির্ভরযোগ্য সূত্রে উদ্ধৃত হয়েছে। এ পর্যায়ে বর্ণিত নেষেধমূলক হাদীসগুলো সমালোচনার আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত। তার কোন একটিও এমন নয়, যার সম্পর্কে হাদীস বিজ্ঞানী ও ফিকাহবিদগণ আপত্তি তোলেন নি। কাযী আবূ বকর ইবনুল আরাবী বলেছেনঃ গান হারাম হওয়ার পর্যায়ে কোন একটি হাদীসও সহীহ্ নয়। ইবনে হাজম বলেছেনঃ এ পর্যায়ের সব বর্ণনাই বাতিল ও মনগড়া রচিত।
গান এ বাদ্যযন্ত্র সাধারণত উচ্চ পর্যায়ের বিলাস-ব্যসন ও শান-শওকতপূর্ণ অনুষ্ঠানাদিতে, মদ্যপানের আসরে ও রাত্রি জাগরণের মজলিসসমূহে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এ করণে বহু আলিম তাকে হারাম বা মাকরূহ বলেছেন। আর অন্যান্য আলিমগণ মনে করেন, কুরআনের ভষায় এ গান-বাজনা সেই ‘লাহউল হাদীস’ যার কথা এ আয়াতে বলা হয়েছেঃ ( আরবি*******************)
লোকদের মধ্যে এমনও আছে, যারা ‘লাহউল-হাদীস’ ক্রয় করে, যেন তারা লোকদের আল্লাহর পথ থেকে কোনরূপ ইলম ছাড়াই ভ্রষ্ট করে দিতে পারে। আর যেন তারা আল্লাহর পথকে ঠাট্টা ও বিদ্রূপ করে। এ লোকদের জন্যে খুবই অপমানকর আযাব রয়েছে।
ইবনে হাজম বলেছেন, যে ব্যক্তি ‘লাহউল-হাদীস’ গ্রহণ করে এ আয়াতটি তার পরিচিতিস্বরূপ বলেছে যে, সে ব্যক্তি নিঃসন্দেহে কাফির। কেননা সে আল্লাহর পথকে ঠাট্টাও বিদ্রুপ করে। সে যদি কোন বই ক্রয় করে লোকদের ভ্রষ্ট করে ও আল্লহর পথকে ঠাট্টা ও বিদ্রূপ করে, তাহলে সে নিঃসন্দেহে কাফির। আল্লাহ্ তা’আলা উপরিউক্ত আয়াতে তার দোষের কথা বলেছেন। সে লোকের দোষ বলেন নি, নিন্দা করেন নি, যে লোক ‘লাহউল হাদীস’ কে লোকদের ভ্রষ্ট করার উদ্দেশ্যে নয়, কেবলমাএ খেলা তামাসা-স্ফূর্তি করার উদ্দেশ্যে খরিদ করে এবং তার দ্বারা স্বভাব মেজাজের সুষ্টতা ও সন্তুষ্টি বিধান করে।
যাঁরা বলেন যে, গান ঠিক নয়, তা অবশ্যই ভ্রষ্টতা, তাদের প্রতিবাদ করে ইবনে হাজম লিখেছেন, রাসূলে করীম (সা) বলেছেন, কার্যাবলীর ভাল-মন্দ নির্ভর করে নিয়তের ওপর। কাজেই যে লোক এ নিয়তে গান শুনল যে, তার দ্বারা গুনাহের কাজে উৎসাহ পাওয়া যাবে, তাহলে সে ফাসিক। পক্ষান্তরে যে লোক স্বভাব-মেজাজের সুষ্ঠতা লাভের উদ্দেশ্যে শুনল, আল্লাহনুগত্যমূলক কাজে শক্তি সাহস পাওয়ার এবং ভাল ও সৎকাজে আগ্রহ ও উৎসাহ বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে শুনল, তার এ কাজ নিশ্চয়ই অন্যায় বা বাতিল নয়। আর যে ব্যক্তি না আল্লাহনুগত্যের নিয়তে শুনল, না নাফরমানী নিয়তে, তার এ কাজ নিষ্ফল কাজের পর্যায়ে গণ্য। তা আল্লহ্ মাফ করে দেবেন। যেমন কারো বাগানে, খোলা মাঠে বা নদী-তীরে পায়চারী করার জন্যে বের হওয়া শুধু প্রাতঃ ভ্রমণ ও সন্ধ্যাকালীন বিহার করার উদ্দেশ্যে নিজ বাড়ির দরজায় বসে থাকে আমোদ-প্রমোদ ও শিথিলতা সম্পাদনের জন্যে অথবা নিজের কাপড় হড়িৎ, সবুজ বা অন্য কোন বর্ণে রঞ্জিত করা ইত্যাদি।
তবে গানের ব্যাপারে কয়েকটি জিনিসের দিকে অবশ্যই লক্ষ রাখতে হবেঃ
১. গানের কথা বা বিষয় বস্তু ইসলামী শিক্ষা ও ভাবধারা পরিপন্থী হতে পারবে না। মদ্যের গুণ বর্ণনাকারী বা মদ্যপানে আমন্ত্রণকারী গান অবশ্যই হারাম। কেননা তা থেকে হারাম কাজ করার প্রেরণা পাওয়া যায়।
২. অনেক সময় দেখা যায়, গান হয়ত ইসলামী ভাবধারা পরিপন্থী নয়, কিন্তু গায়কের সঙ্গীত-ঝংকার ও পদ্ধতি হালালের সীমা ডিঙ্গিয়ে হারামের পর্যায়ে পৌঁছে দেয়। যেমন খুব হাস্য-লাস্যময়ী ও লজ্জাষ্কর অঙ্গভঙ্গি সহকারে, হেলে দুলে, নির্লজ্জতার ধরন অনুসরণ এবং হৃদয়াবেগে তুফানের উত্তেজনা ও আলোড়নের সৃষ্টি করে, লালসা উদ্দীপক ও দুর্ঘটনা সঙ্ঘটকরূপে তা উপস্থাপন করে।
৩. দ্বীন ইসলাম সর্বব্যাপারেই বাড়াবাড়ি ও সীমালংঘনমূলক আচরণের বিরোধী। ইবাদতের ব্যাপারেও এই কথা। লাহউন-এর ব্যাপারেও কোনরূপ সীমালঙ্ঘন বরদাশত যোগ্য নয়া। তাতে খুব বেশি সময় ব্যয় করা কখনই উচিত নয় অথচ সময়ই হচ্ছে জীবনের মূলধন।
সন্দেহ নেই, বৈধ কাজে সীমালংঘন ও বাড়াবাড়ি করা হলে প্রকৃত কর্তব্য সম্পাদনের ত্রুটি থাকা খুবই স্বাভাবিক। এ কারণে যথার্থই বলা হয়েছেঃ ( আরবি*******************)
বাড়াবাড়িকে আমি এমন অবস্থায় দেখেছি যে, তার সম্মুখে প্রকৃত সত্য মার খেয়ে যাচ্ছে, বিনষ্ট হচ্ছে।
৪. কোন কোন গান শুনে ব্যক্তি নিজের কাছ থেকেই ফতোয়া পেয়ে যেতে পারে, সে গান শুনে হৃদয়াবেগ যদি উত্তেজিত হয়ে উঠে থাকে এবং তাতে বিপদ ঘটাতে উদ্বুদ্ধ করে থাকে- আধ্যাত্মিকতার পরিবর্তে পাশবিকতার প্রাধান্য হতে দেখা যায়, তাহলে তা অবশ্যই পরিহার করা উচিত এবং যে দুয়ার থেকে বিপদের হাওয়া আসে, তা বন্ধ করে দেয়া কাঞ্ছনীয়।
৫. এ ব্যাপারে সকলেই একমত যে, যে গানের সাথে মদ্যপান, ফষ্টিনষ্টি ও চরিত্রহীনতার মতো কোন হারাম জিনিসের সংমিশ্রণ হয়, সে গান হারাম। এ বিষয়ে নবী করীম (সা) কঠিন আযাবের দুঃসংবাদ শুনিয়েছেন। তিনি বলেছেনঃ ( আরবি*******************)
আমার উম্মতের কিছু সংখ্যক লোক মদ্যপান করবে এবং তার আসল নামের পরিবর্তে নতুন ও ভিন্নতর নাম রেখে দেবে। তাদের শীর্ষদেশে বাদ্য বাজানো হবে, গায়িকারা গান গাইবে। আল্লাহ্ জমিনে তাদের ধ্বসে দেবেন এবং ওদের কতিপয়কে বানর ও শূকর বানিয়ে দেবেন। (ইবনে মাজাহ)
এই কথানুযায়ী বিকৃতিটা আকার-আকৃতিতে আসা জরুরী নয়। এ বিকৃতি মন-মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গির দিক দিয়েও হতে পারে অর্থাৎ মানব দেহের বানরের আত্মা ও মানসিকতা এবং শূকরের রূহ বিরাজ করবে। অন্য কথায় আকৃতিতে মানুষ কিন্তু প্রকৃতিতে বানর ও শূকর। [ মনে রাখতে হবে গ্রন্থকার এখানে গান মুবাহ হওয়ার পক্ষে যা লিখেছেন তার জন্যে এমন সব শর্তের উল্লেখ করেছেন, যা পালন করা খুবই দুষ্কর। অথচ আমাদের দেশে ও সমাজে সাধারণত যে সব গান শোনা বা শোনানো হয়, যে সব ফিল্মের গান প্রচার করা হয় তা উক্ত শর্তে উত্তীর্ণ হতে পারে না। কাজেই এগুলো জায়েয হওয়ার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। কেননা এগুলো হচ্ছে নির্লজ্জতা ও যৌনতা প্রচার-প্রসারের বড় মাধ্যম। নৈতিকতার জন্যে তা বড়ই মারাত্মক। গায়ক, গায়িকারা গান গেয়ে নারী-পুরুষদের মুগ্ধ বিমোহিত করে। অথচ ইসলাম নৈতিক পবিত্রতা ও নিষ্কলুষতার ওপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করেছে। কোন নারীর পরপুরুষের সাথে অথবা পুরুষের পরনারীর মধুমিশ্রিত মোলায়েম কন্ঠে কথা বলাও জায়েয রাখা হয়নি। কুরআন মজীদে তা স্পষ্টভাবে ঘোষিত হয়েছে। ভিন পুরুষ মেয়েলোকের মধুর কন্ঠস্বর স্বাদ গ্রহণকে ইসলামে ব্যভিচার বলে অভিহিত করা হয়েছে। অতএব এসব গান যে হারাম তাতে কোনই সন্দেহ থাকতে পারে না। তবে প্রকৃত ইসলামী ভাবধারা সৃষ্টিকারী ও জিহাদী তেজোবীর্য উদ্বোধক গানের মুবাহ হওয়াও সর্বজনস্বীকৃত।-অনুবাদক ]
জুয়া-সুরা-সঙ্গী
ইসলামে বহু কয় প্রকারের খেলা ও আনন্দ স্ফূর্তির অনুষ্ঠানকে জায়েয ঘোষণা করা হয়েছে। সেই সঙ্গে যে সব খেলার সাথে জুয়া মিশ্রিত, যে সব খেলায় আর্থিক লাভ-লোকসানের ব্যবস্থা অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে শামিল, তা সবই হারাম ঘোষিত হয়েছে। এ পর্যায়ে রাসূলে করীম (সা)-এর সেই কথাটি স্মরণীয়, যাতে তিনি বলেনঃ কেউ যদি বলে যে, আস, তোমার সাথে জুয়া খেলি, তাহলে তার এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কাফফারা স্বরূপ সাদকা দেয়া কর্তব্য।
অতএব জুয়াকে অর্থোপার্জনের উপায় হিসেবে যেমন গ্রহণ করা মুসলমানের জন্য জায়েয নয়, তেমনি তা খেলা, মনের সান্তনা-পরিতৃপ্তি ও অবসর বিনোদনের উপায়রূপেও গ্রহণ করা যেতে পারে না।
জুয়া খেলার হারাম হওয়ার পেছনে অতীব অকাট্য যুক্তি ও উচ্চতর লক্ষ্য নিহিত।
১.মুসলমানের পক্ষে অর্থোপার্জনে আল্লাহর বেঁধে দেয়া নিয়ম ও পথ অনুসরণ করা একান্ত কর্তব্য। কার্যকারণের মাধ্যমে ফল লাভ করতে চাওয়া উচিত। ঘরে তার দরজা দিয়েই প্রবেশ করতে হবে, অবলম্বিত কারণ বা কাজের ফল চাইতে হবে – এটাই ইসলামের লক্ষ্য।
জুয়া-লটারীও মানুষের মধ্যে ভাগ্য ও ভিত্তিহীন আশা-আকাংখার ওপর নির্ভরতা গ্রহণের প্রবণতা জাগায়। আল্লাহ্ অর্থোপার্জনের জন্যে যেসব চেষ্টা-প্রচেষ্টা, শ্রম ও
কার্যকারণ অবলম্বনের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন ও আদেশ করেছেন, জুয়া তা গ্রহণের জন্যে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে না।
২. ইসলাম মুসলমানের জন্যে অপর লোকের মাল হারাম করে দিয়েছে, অতএব তার কাছ থেকে তা নেয়া যেতে পারে কেবলমাত্র শরীয়ত-সম্মত বিনিময় মাধ্যমে অথবা সে নিজের খুশিতে যদি দান করে বা হেবা উপহার দেয় তবেই তা নেয়া যেতে পারে। এছাড়া অন্য যে কোন উপায়ে তা নেয়া সম্পূর্ণ হারাম। এ দৃষ্টিতেই বলা যায়, জুয়া হচ্ছে পরের ধন অপহরণের বাতিল ও হারাম পদ্ধতি।
৩. জুয়া খেলা খোদ জুয়াড়ী ও খিলোয়াড়দের মধ্যে গভীর শত্রুতা ও হিংসা-প্রতিহিংসার সৃষ্টি করে দেয় অতি স্বাভাবিকভাবেই এবং এতে বিস্ময়ের কিছু নিই। মুখের কুথায় ও বাহ্যত মনে হবে তারা পরস্পরের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন, কিন্তু আসলে তাদের মধ্যে জয়ী-বিজয়ীর দ্বন্দ্ব ও হিংসা-প্রতিহিংসার আগুন দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে প্রতি মুহুর্তে। আর বিজিত চুপ হয়ে থাকলেও ক্রোধ, আক্রোশ ও ব্যর্থতার প্রতিহিংসায় সে জ্বলতেই থাকে। কেননা সে বিজিত এবং তার সব কিছুই সে খুইয়েছে। আর যদি সে ঝগড়া ও বাকবিতণ্ডা করতে শরু করে, তাহলে তার অন্তরে সেই চাপা ক্ষোভ তাকে প্রতিশোধ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে তোলে।
৪. খেলায় বাজি হেরে গেলে বিজিত ব্যক্তি আবার খেলতে শুরু করে। তখন সে আশা করতে থাকে যে, সে যা হারিয়েছে তা তো ফেরত পাবেই। সে সেই ধ্যানে মশগুল হয়। অপরদিকে বিজয়ী ব্যক্তির জিহ্বায় লোভ লেগে যায়, মুখে পানি টসটস করতে থাকে । সেজন্যে সে বারবার খেলতে বাধ্য হয়। আরও বেশি বেশি অর্থ লুণ্ঠনের লোভ তাকে অন্ধ ও অপরিণামদর্শী বানিয়ে দেয়।
খেলার ধারাবাহিকতা এ রূপেই অবিচ্ছিন্নভাবে চলতে থাকে। জয়ী বা বিজিত কেউ কাউকে ছাড়তে প্রস্তুত হয় না।
৫. এ কারণে জুয়া খেলার নেশা যেমন ব্যক্তির জন্যে বিপদ ডেকে আনে, তেমনি সমাজেও কঠিন বিপর্যয়ের সৃষ্টি করে। এ নেশা মানুষের শুধু ধন-সম্পদই হরণ করে না, তার জীবনটাও বরবাদ করে দেয়।
এই খেলা খেলোয়াড়দের সম্পূর্ণ অকর্মন্য বানিয়ে দেয়। তারা জীবনে অনেক কিছুই গ্রহণ করে কিন্তু জীবনকে দেয় না কিছুই। তারা ভোগ করে উৎপাদন করে না। জুয়াড়ী জুয়া খেলায় এতই মত্ত হয়ে যায় যে, তার নিজস্ব দায়িত্ব কর্তব্যের কথা সম্পূর্ণ ভুলে যায়। বান্দার প্রতি আল্লাহর আরোপিত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করা তার পক্ষে সম্ভব হয় না। তারা নিজের পরিবার, সমাজ ও জনগণের কথা তার স্মরণ আসা অসম্ভব থেকে যায়। এ ধরনের লোক নিজের স্বার্থের বিনিময়ে তার নিজের দ্বীন ও ধর্ম, ইজ্জত-হুরমাত ও দেশকে বিক্রয় করে দিতেও কুণ্ঠিত হয় না। কেননা জয়ার আকর্ষণ এতই তীব্র যে, তর সম্মুখে জুয়া খেলার প্রতি প্রেম ও আসক্তি এত অধিক ও তীব্র হয় যে, সে সব ব্যাপারে ও সব ক্ষেত্রে জুয়া খেলতে শুরু করে দেয়। এমনকি সে এক অনির্দিষ্ট ও অনিশ্চিত উপার্জনের আশায় পড়ে তার নিজের ইজ্জত ও মর্যাদা এবং তর নিজের ও গোটা জাতির আকীদা-বিশ্বাসের সঙ্গেও সে জুয়া খেলতে শুরু করে দেবে, এটাই স্বভাবিক পরিণতি।
কুরআন মজীদ তার একটি আয়াত ও আদেশের মধ্যে মদ্য ও জুয়াকে একত্রিত করে ও একই ভাবে হারাম ঘোষণা করে কতো যে উচুমানের বাস্তবদর্শিতার প্রমাণ উপস্থাপিত করেছে, তা বিশ্লেষণ করার অপেক্ষা রাখে না। কেননা এ দুটির ক্ষতি ও মারাত্মক অপকারিতা সমানভাবে প্রবর্তিত হয় ব্যাক্তি, পরিবার, দেশ ও চরিত্র সবকিছুর ওপর। জুয়ার নেশা মনের নেশার মতোই সর্বাত্মক ও মারাত্মক। উপরন্তু এর একটি যেখানে তথায় অপরটির উপস্থিতি অবধারিত।
কুরআন বলেছে, এ দুটি শয়তানের কাজ এবং কুরআন এ দুটোকে ‘স্থান বলিদান’ ও ‘তীর দিয়ে ভাগ্য জানা’- এ দুটি কাজের সঙ্গে একত্রে উল্লেখ করে এ সবগুলো অত্যন্ত বড় বড় পাপ প্রতিষ্ঠান বলে পরিহার ও বর্জন করে চলার নের্দেশ দিয়েছে। এ পর্যায়ে কুরআনের আয়াতটি হচ্ছেঃ ( আরবি*******************)
হে ঈমানদার লোকেরা! মদ্য, জুয়া, বলিদানের স্থান ও পাশা-ছক্কা- এসব অপবিত্র মলিনতা পংকিল শয়তানী কাজ। এগুলো পরিহার কর, যেন তোমরা কল্যাণ লাভ করতে পার। শয়তান তো শুধু এই চায় যে, মদ্য ও জুয়ায় তোমাদের মগ্ন ও নিমজ্জিত করে তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও হিংসা-বিদ্বেষের সৃষ্টি করে দেবে এবং তোমাদের আল্লাহর স্মরণ ও নামায থেকে দূরে সরিয়ে রাখবে। এমতাবস্থায় তোমরা এসব কাজ থেকে বিরত থাকবে কি?
লটারীও এক প্রকার জুয়া
লটারীও এক প্রকারের জুয়া! তাকে সাধারণ জিনিস মনে করা এবং জনকল্যানমূলক প্রতিষ্ঠান ও মানবীয় স্বার্থের নামে তাকে জায়েয মনে করা কোনক্রমেই সহীহ কাজ হতে পারে না। যাঁরা এ ধরনের কাজের জন্যে লটারীকে জায়েয মনে করেন, তাঁরা হারাম নৃত্য ও হারাম শিল্প ইত্যাদির দ্বারা এসব উদ্দেশ্যে অর্থ সংগ্রহ করতেও পিছপা হন না। কিন্তু তা সুস্থ বিবেকসম্পন্ন কোন মানুষের কাছেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। আমরা তাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাইঃ ( আরবি*******************)
আল্লাহ্ তা’আলা পবিত্র পাক। তিনি পবিত্র জিনিসই কবুল করেন। (হাদীস)
এ লোকেরা মনে করে, জনগণের মধ্যে মানবীয় সহানুভূতি ও কল্যাণমূলক কাজের কোন ইচ্ছা বা প্রবণতা নেই। নেক কাজের কোন তাৎপর্যই তারা বুঝে না। কর্তব্য বোধ বলতেও তাদের কেছুই অবশিষ্ট নেই । আছে শুধু পাশবিক কামনা-বাসনা-লালসা। এ করণে জুয়া ও নিষিদ্ধ ধরনের খেলা ইত্যাদির তামাসাকে উপায় না বানিয়ে কোন কাজই করা যাবে না। কিন্তু ইসলাম মুসলমান সমাজ সম্পর্কে এই মনোভাব ও দৃষ্টিকোণ সমর্থন করে না এবং কোন নেক কাজের জন্য এ সব উপায় অবলম্বনের অনুমতি দেয় না। নেক ও পবিত্র উদ্দেশ্যের (Noble cause) জন্যে পবিত্র পন্থা ও উপায় অবলম্বনের জন্যে ইসলামের তাগিদ রয়েছে। আর সে উপায় হচ্ছে নেক কাজের আহ্বান, মানবীয় পবিত্র ভাবধারা জাগ্রত করা এবং আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি ঈমানের ভিত্তিতে কল্যাণময় কাজের আমন্ত্রণ।
সিনেমা দেখা
এ কালের সিনেমা-থিয়েটার সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিকোণ কি, সিনেমা থিয়েটারে প্রবেশ করা ও দেখা মুসলমানদের জন্যে জায়েয কিনা, তা অনেকেই জানতে চান।
সিনেমা-থিয়েটার ও এ ধরনের অন্যান্য জিনিস যে চিও-বিনোদনের বড় মাধ্যম, তা অস্বীকার করা যায় না। সেই সাথে এতেও কোন সন্দেহ নেই যে, এসব আধুনিক মাধ্যমকে ভাল ও মন্দ উভয় ধরনের কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে।
ইসলামের দৃষ্টিকোণে বলা যায়, সিনেমা বা ফিল্মে মূলত ও স্বতঃই কোন দোষ বা খারাপী নেই। তা কি কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে, তা দিয়ে কি উদ্দেশ্য সাধন করতে চাওয়া হচ্ছে, সেটাই আসল প্রশ্ন। এ কারণে এই গ্রন্থকারের মতে সিনেমা বা ফিল্ম ভাল ও উত্তম জিনিস। নিম্নোদ্ধৃত শর্তসমূহ সহকারে কাজে লাগালে তা খুবই কল্যাণকর হতে পারে।
প্রথমতঃ যে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে তার দ্বারা প্রতিবিম্বিত ও প্রতিফলিত করা হয় তা যেন নির্লজ্জতা-নগ্নতা-অশ্লীলতা ও ফিসক-ফুজুরী থেকে সম্পর্ণ মুক্ত থাকে। সে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যও যেন ইসলামী আকীদা বিশ্বাস, শরীয়ত ও তার নিয়ম-কানুনের পরিপন্থী না হয়। উপস্থাপিত কাহিনী যদি দর্শকদের মধ্যে হীন যৌন আবেগ জাগরণকারী, গুনাহের কাজে প্রবণতা সৃষ্টিকারী, অপরাধমূলক কাজে উদ্বুদ্ধকারী কংবা ভুল চিন্তা-বিশ্বাস প্রচলনকারী হয়, তাহলে এ ধরনের ফিল্ম অবশ্যই হারাম। তা দেখা কোন মুসলমানের জন্যেই হালাল বা জায়েয নয় কিংবা তা দেখার উৎসাহও দেয়া যেতে পারে না।
[ আমাদের সব দেশে যে সিনেমা প্রদর্শিত হয় তাতে এসব ভুল ও মারাত্মক উদ্দেশ্য থেকে মুক্ত কোন ফিল্ম হয় বলে মনে করা যায় না। সাধারণত যুবক-যুবতীদের পেম ও নারী নিয়ে দ্বন্দ্ব-এ সবই ফিল্মের আসল প্রতিপাদ্য। পুরুষ নারীদের রূপ ও যৌবন প্রদর্শনই এগুলোর প্রধান উপজীব্য, চাকচিক্য ও আকর্ষণ। সেই সাথে থাকে চিত্তহারী নৃত্য ও সঙ্গিত। সিনেমার প্রেমভরা লজ্জা-শরম বিধ্বংসী ও চরিত্র হানিকর কথোপকথন ও নৈতিক বিপর্যয়ের মূলে এ কালের এ ছবি-সিনেমার অবদান অনেক বেশি। কাজেই তা কোনক্রমেই জায়েয হতে পারে না। তবে কোন ফিল্ম যদি বাস্তবিকই এসব কদর্যতা মুক্ত ও কল্যাণময় ভাবধারা সম্পন্ন হয়, তবে তাতে কোন আপত্তি থাকর কথা নয়। -অনুবাদক ]
দ্বিতীয়তঃ কোনরূপ দীনী ও বৈষয়িক দায়িত্ব পালনের প্রতি যেন উপেক্ষা প্রদর্শিত না হয়। বিশেষ করে পাঁচ ওয়াক্ত নমায- যা মুসলিম মাত্রের ওপরই ফরয- আদায় করতে কোন বিঘ্ন দেখা না দেয়। ছবি দেখার কারণে নামায বিশেষ করে মাগরিবের নামায যেন বিনষ্ট না হয়। তাহলে তা দেখা কিছুতেই জায়েয হবে না। তাহলে তা কুরআনের এ আয়াতের মধ্যে পড়বেঃ ( আরবি*******************)
ধ্বংস সেসব নামাযীর জন্যে যারা নিজেদের নামাযের ব্যাপারে গাফিল বা উপেক্ষা প্রদর্শনকারী। (সূরা মাঊন)
এ আয়াতের ( আরবি*******************) শব্দের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, নামায সময়মত না পড়লেই তার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করা হয়। আর পূর্বে উদ্ধৃত আয়াতে মদ ও জুয়া হারাম হওয়ার অন্যতম কারণ স্বরূপ বলা পয়েছে যে, এ দুটো কাজ আল্লাহর যিকির ও নামায ইত্যাদি থেকে বিরত রাখে, সে দিকে মনোযোগী হতে দেয় না।
তৃতীয়ত সিনেমা দর্শকদের কর্তব্য ভিন্ ও গায়র মুহাররম নারী-পুরুষদের সাথে সর্বপ্রকার সংমিশ্রণ বা ঢলাঢলি- ঢলাঢলি পরিহার করে চলা, এ ধরনের স্থান বা অবস্থা এড়িয়ে চলা। কেননা তাতে মানুষের নৈতিক বিপদ ঘটতে পারে, সেজন্যে লোকদের মনে সন্দেহের উদ্রেক হতে পারে বিশেষত এ কারণে যে, সিনেমা সাধারণত অন্ধকারেই দেখা হয়। পূর্বে এ হাদীসটি এক স্থানে উদ্ধৃত হয়ে থাকলেও এখানেও তা স্মরণীয়ঃ ( আরবি*******************)
তোমাদের কারো মস্তকে সুঁচ বিদ্ধ হওয়াও কোন অ-হালাল নারীর স্পর্শ হওয়ার তুলনায় অনেক উত্তম। (বায়হাকী, তিবরানী)
সামাজিক সম্পর্ক
ইসলাম সমাজের ব্যক্তিদের পারস্পরিক সম্পর্ককে দুটো ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছে।
একটি হচ্ছে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক। এ সম্পর্ক বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে অত্যন্ত দৃঢ ও অবিচ্ছিন্ন বন্ধনের কাজ করে। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে অধিকার ও মান-মর্যাদা সংবরক্ষণ। প্রত্যেক ব্যক্তির রক্ত, মান-সম্মান ও ধন-মালের নিরাপত্তা ও সম্মানার্হতা। যেসব কথা ব্যবহার-আচরণ বা কাজ এই ভিত্তিদ্বয়কে ক্ষুণ্ণ বা ক্ষতিগ্রস্ত করে, খারাপভাবে প্রভাবিত করে তা ইসলামের দৃষ্টিতে হারাম। এ ক্ষতি বৈষয়িক দৃষ্টিতে হোক বা সাংস্কৃতিক দৃষ্টিতে, তাতে কোন পার্থক্য হয় না। তা যে ধরনের যতটা মাত্রারই হোক-না-কেন, সেই দৃষ্টিতে ততটা মাত্রায়ই তা হারাম হবে। নিম্নোদ্বৃত আয়াতে সেসব হারাম জিনিসের উল্লেখ করা হয়েছে, যা পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব ও মানবীয় মান-মর্যাদার পক্ষে ক্ষতিকরঃ ( আরবি*******************)
মুমিন পরস্পরের ভাই। অতএব আপন ভাইয়ের মধ্যে সন্ধি-সমঝোতা করিয়ে দাও। আর আল্লাহকে ভয় করো, যেন তোমাদের প্রতি দয়া করা যায়। হে ঈমানদার লোকেরা! না কোন পুরুষ অপর পুরুষদের অপমান সুচক ঠাট্টা-বিদ্রুপ করবে,- কেননা, তারাও তো তার তুলনায় ভাল হতে পারে! তোমরা পরস্পরকে কষ্ট বা দুঃখ দেবে না, পরস্পর খারাপ উপাধিতে ডাকবে না। ঈমান গ্রহণের পর ফাসিকী অত্যন্ত নিকৃষ্ট পর্যায়ের নাম। আর যারা তাওবা করে বিরত হবে না, তারাই জালিম।
হে ঈমানদার লোকেরা! অনেক ধরনের ভিত্তিহীন ধারণা থেকে দূরে থাক। কোন কোন ভিত্তিহীন ধারণা সুস্পষ্ট গুনাহ, আর তোমরা লোকদের দোষত্রুটি খোঁজ করে বেড়িও না, কেউ যেন কারো অনুপস্থিতিতে তার দোষ প্রচার না করে। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইর গোশত ভক্ষণ করা পছন্দ করবে? তোমরা তো তা ঘৃণাই কর। আর আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর। নিশ্চিত জানিও আল্লাহ্ বড়ই তাওবা কবুলকারী দয়াশীল। (সূরা হুজরাতঃ ১০-১২)
প্রথম আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেন, মুমিনরা পরস্পর ভাই। এতে মানবীয় ভ্রাতৃত্বের সাথে সাথে দ্বীনী ভ্রাতৃত্বও বর্তমান। দুটো একসাথে একত্রিত ও সমম্বিত। এ ভাতৃত্বের দাবি হচ্ছে, তারা পরস্পর নিঃসম্পর্ক বা অপরিচিত হয়ে থাকবে না। পরস্পরের মধ্যে গভীর একাত্মতা থাকা একান্তই বাঞ্ছনীয়। পরস্পর বিচ্ছিন্ন নয়, ঘনিষ্ঠভাবে মিলিত হয়ে থাকবে। পরস্পর কোন শত্রুতা, হিংসা-বিদ্বেষ থাকবে না, থাকবে অকৃত্রিম ভালবাসা, দয়া-সহানুভূতি। পরস্পরের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও মতপার্থক্য থাকবে না, সম্পূর্ণ একমত হয়ে কাজ করবে। হাদীসে তাই বলা হয়েছেঃ ( আরবি*******************)
তোমরা পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষে লিপ্ত হবে না, কেউ কারো পিছনে পড়ে যাবে না- কেউ কারো দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে না। পারস্পরিক ক্রোধ ও অসন্তোষের প্রশ্রয় দেবে না; বরং পারস্পরিক আল্লাহর বান্দা ও ভাই হয়ে থাকবে।
মুসলমান ভাইর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবে না
এ কারণে কোন মুসলিম ভাইর প্রতি নির্মম ও পাষাণবৎ ব্যবহার করতে, বয়কট করতে ও তার প্রতি বিমুখ হয়ে থাকতে নিষেধ ও হারাম করা হয়েছে। দুজন মুসলমানের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষের সৃষ্টি হলে ক্রোধ দমনের জন্যে মাত্র তিনটি দিনের সময় দেয়া হয়েছে। অতঃপর পারস্পরিক সন্ধি সমঝোতা ও মিলমিশ সৃষ্টি ও ক্রোধ হিংসা সৃষ্টির কারণসমূহ দূর করার জন্যে চেষ্টা করা কর্তব্য। কুরআন মাজীদে মুমিন মুসলমানের গুণ স্বরূপ বলা হয়েছেঃ ( আরবি*******************)
মুমিনদের জন্যে অত্যন্ত নম্র বিনয়ী সহানুভূতি সম্পন্ন। (সূরা মায়িদাঃ ৫৪)
নবী করীম (সা) বলেছেনঃ ( আরবি*******************)
কোন মুসলমানের পক্ষে তার ভাইকে তিন দিনের অধিক সময়ের জন্যে সম্পর্কহীন করে রাখা হালাল বা জায়েয নয়। তিন দিন অতিবাহিত হয়ে গেলে তার সাথে তার সাক্ষাৎ করা ও তাকে সালাম দেয়া কর্তব্য। যদি সে সে সালামের জবাব দেয়, তাহলে দুজনই সাওয়াবে শরীক হলো। আর জবাব না দিলে সে-ই গুনাহগার হবে এবং সালামদাতা সম্পর্কচ্ছেদের গুনাহ হতে রক্ষা পেয়ে যাবে। (আবূ-দাউদ)
রক্ত সম্পর্কের আত্মীয়ের সাথে আত্মীয়তা রক্ষা করাকে ইসলাম ওয়াজিব ঘোষণা করেছেল। এ সম্পর্ক যত গভীর সেই অনুপাতে তা রক্ষা করার তাগিদও ততই বেশি ও বলিষ্ঠ। এ সম্পর্ক ছিন্ন করা কঠিনভাবে হারাম। আল্লাহ্ তা’আলা ইরশাদ করেছেনঃ ( আরবি*******************) এবং ভয় কর আল্লাহকে, যাঁর দোহাই দিয়ে তোমরা পরস্পরের কাছে নিজের হক বা অধিকারের দাবি কর। আর নিকটাত্মীয়তার সম্পর্ককেও ভয় কর-রক্ষা কর। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তোমাদের পর্যবেক্ষণে রত। (আন-নিসাঃ ১)
এই নিকটাত্মীয়তার গুরুত্ব এবং আল্লহর কাছে তার মূল্য ও মর্যাদা বোঝাবার জন্যে রূপকভাবে বলেছেলঃ ( আরবি*******************) রেহম- রক্ত সম্পর্কের নিকটাত্মীয়তা আরশের সাথে ঝুলে থেকে বলেঃ যে আমাকে রক্ষা করল, আল্লাহও তাকে রক্ষা করবেন। আর যে আমাক ছিন্ন করল, আল্লাহও তাকে ছিন্ন করবেন। (বুখারী, মুসলিম)
বলেছেনঃ ( আরবি*******************)
(রক্ত সম্পর্ক) ছিন্নকারী কখনই বেহেশতে যাবে না। (বুখারী, মসলিম)
এ হাদীসটির ব্যাখ্যায় আলিমগণ দুটো কথা বলেছেন। একটি হচ্ছে রক্ত সম্পর্ক ছিন্নকারী, আর অপরটি হচ্ছে ডাকাত, ছিনতাইকারী- পথে-ঘাটে হত্যাকারী অর্থাৎ এ দুটো লোক একই পর্যায়ের অপরাধী
রক্ত সম্পর্কের ব্যাপারটি এরূপ নয় যে, একজন নিকটাত্মীয় অপর নিকটাত্মীয়ের সাথে সমতা আচরণ করবে। সে রক্ষা করলে তবে এ-ও রক্ষা করবে, সে ভাল ব্যবহার করলে এ-ও ভাল ব্যবহার করবে, এরূপ জেদাজেদি অবাঞ্ছনীয়। এটা তো স্বাভাবিক ব্যাপার। ওয়াজিব হচ্ছে, কেউ সম্পর্ক ছিন্ন করলেও সে তা রক্ষা করে চলবে। নবী করীম (সা) বলেছেনঃ (আরবি*******************) ছেলায়ে রেহমী রক্ষাকারী সে নয়, যে সমান সমান ব্যবহার করে। বরং ছেলায়ে রেহমী রক্ষাকারী হচ্ছে সে, যে তা ছিন্নকারীর সাথে তা রক্ষা করে। (বুখারী)
এ সম্পর্ক ছিন্নকরণ ও বয়কট যদি আল্লাহর জন্যে, আল্লাহর পথে এবং প্রকৃত সত্যের জন্যে না হয়, তাহলেই এ কথা। অন্যথায় ঈমানের দৃঢ়তা সাধনের বড় উপায় হচ্ছে, আল্লাহর জন্যে ভালবাসা, আল্লাহর কারণে হিংসা বিচ্ছেদ।
নবী করীম (সা) এবং তাঁর সাহাবিগণ তাবুক যুদ্ধে পিছনে পড়ে থাকা লোকদের সাথে পঞ্চাশ দিন সম্পর্কছিন্ন করে রেখেছিলেন। শেষ পর্যন্ত এ শেষোক্ত লোকদের জীবন অতিষ্ট হয়ে উঠল, প্রাণান্তকর অবস্থা দেখা দিল। কেউ তাদের সঙ্গে ওঠা-বসা করত না, কথা বলত না, সালামও দিত না। অতঃপর আল্লাহ্ তাদের তাওবা কবুল করার কথা বলে আয়াত নাযিল করেন।
নবী করীম (সা) তাঁর কোন কোন বেগমের সাথে চল্লিশ দিন পর্যন্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে রেখেছিলেন। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা) তার পুত্রের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে রেখেছিলেন। শেষ পর্যন্ত সে মরেই গেল। তার কারণ ছিল এই যে, সে রাসূলে করীম (সা)-এর একটি হাদীসকে মোটেই আমল দেয়নি, যা তিনি রাসূল থেকে বর্ণনা করেছিলেন। সে হাদীসটিতে রাসূলে করীম (সা) মেয়েদেরা মসজিদে যাওয়া থেকে নিষেধ করেছিলেন। ( আরবি*******************)
কিন্তু এ পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও সম্পর্কচ্ছেদ যদি দুনিয়ার বৈষয়িক কোন কারণে হয়, নিতান্তই স্বার্থের দ্বন্দ্বের দরুন হয় তাহলে তা খুবই অকিঞ্চিৎকর জিনিস, একজন মুসলমান তার এক মুসলমান ভাইর সাথে কিভাবে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হতে পারে, যখন তার ফলে আল্লাহর মাগফিরাত ও রহমত থেকে বঞ্চিত থাকার আশংকা রয়েছে? সহীহ হাদীসে বলা হয়েছেঃ ( আরবি*******************)
জান্নাতের দ্বার সোমবার ও বৃহস্পতিবার খুলে দেয়া হয়। অতঃপর আল্লাহ্ মাফ করেন এমন প্রত্যেক বান্দাকে, যে আল্লাহর সাথে একবিন্দু শিরক করে না। তবে সে ব্যক্তিকে ক্ষমা করেন না, যার মধ্যে ও তার ভাইর মধ্যে শত্রুতা ও হিংসা-বিদ্বেষ রয়েছে। তখন আল্লাহ্ বলেনঃ ওদের দুজনকে পরিহার কর, যতক্ষণ না তারা সংশোধিত হয়, ওদের দুজনকে পরিত্যাগ কর যতক্ষণ না তরা সন্ধি সমঝোতা করে নেয়, ওদের দুজনকে ছেড়ে দাও যতক্ষণ না তারা নিজেদের মধ্যে মিলমিশ করে নেয়। (মুসলিম)
আর যে লোকের ন্যায়সঙ্গত অধিকার রয়েছে তার ভাইর কাছে এসে মার্জনা চাইবে এবং তার কর্তব্য তাকে ক্ষমা করে দেয়া এবং ঝগড়া বিবাদ থেকে বিরত হওয়া। ক্ষমা চাইলে ও ওযর পেশ করলে তা প্রত্যাখ্যান করা হারাম। নবী করীম (সা) এরূপ ব্যক্তিকে এই বলে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, কিয়ামতের দিন সে লোক তার সন্নিধানে হাওযে কাওসারে উপস্থিত হতে পারবে না। ( আরবি*******************)
পারস্পরিক সন্ধি সমঝোতাকরণ
দুই বিবাদমান ব্যক্তির কর্তব্য হচ্ছে, ভ্রাতৃসম্পর্কের দাবিতে তাদের পারস্পরিক বিবাদ বিসম্বাদ দূর করা ও সন্ধি-সমঝোতা করে নেয়া। এ যেমন সত্য, তেমনি এ ব্যাপারে সমাজেরও দায়িত্ব রয়েছে। কেননা ইসলামী সমাজ বলতে বোঝায় মানুষের পারস্পরিক সাহায্যকারী পরিপূরক মানব সমষ্টি। অতএব সমাজেরই দুই ব্যক্তিকে পরস্পর দ্বন্দ্বমান ও মারা-মারিতে লিপ্ত দেখবে অথচ সমাজ নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করবে, নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করবে, তা কল্পনাও করা যায় না। তা কোনক্রমেই জায়েয হতে পারে না। কেননা তাহলে তো তারা দুজন ঝগড়া-বিবাদের আগুনে দগ্ধ হতে থাকবে এবং সে আগুন ক্রমশ সম্প্রসারিত হয়ে সমগ্র সমাজটিকে জ্বালিয়ে ভস্ম করে দেবে।
বরং সুস্থ অভিমতসম্পন্ন ও প্রভাব প্রতিপত্তিসম্পন্ন লোকদের কর্তব্য হচ্ছে নিছক সত্য ও ইনসাফের খাতিরে সে বিবাদমান ব্যক্তিদ্বয়ের মধ্যে মীমাংসা করা ও মিলমিশ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে হস্তক্ষেপ করা, চেষ্টা প্রচেষ্টা চালানো এবং তাদের লালসার দাসত্ব করা থেকে দূরে সরে থাকা। আল্লাহ্ তা’আলা এই নির্দেশ দিয়েছেনঃ ( আরবি*******************)
তোমরা তোমাদের ভাইয়ের মধ্যে সন্ধি-সমঝোতা করে দাও এবং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। তাহলে আশা করা যায় যে, তোমাদের প্রতি রহমত করা হবে। (সূরা হুজরাতঃ ১০)
এ সংশোধন ও মিলমিশ বিধানের উচ্চ মর্যাদা এবং পারস্পরিক বিবাদ বিসম্বাদের খারাপ পরিণতির কথা নবী করীম (সা) নিজেই বিশ্লেষণ করে বলেছেনঃ ( আরবি*******************)
নফল নমায, রোযা ও সাদকার তুলনায়ও অধিক উত্তম কাজের কথা কি আমি তোমাদের বলব? সাহাবিগণ বললেন, হ্যাঁ রাসূল, বলুল। বললেন, তা হচ্ছে পারস্পরিক সংশোধন ও মিলমিশ বিধান। কেননা পারস্পরিক বিবাদ-বিসম্বাদ মুণ্ডনকারী জিনিস। আমি বলি না যে, তা চুল মুণ্ডন করে বরং বলি, তা দ্বীনকেই নির্মূল করবে।
অন্যদের বিদ্রুপ করা ঠিক নয়
পূর্বে উদ্ধৃত আয়াতে আল্লাহ্ তা’আলা এমন সব কাজকেই হারাম ঘোষণা করেছেন, যা পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ককে বিনষ্ট করে এবং যা মানুষের মর্যাদা হানিকর।
এ পর্যায়ের প্রথম জিনিস হচ্ছে লোকদের বিদ্রুপ অপমান করা, কাউকে হীন করতে চেষ্টা করা। অতএব আল্লাহকে চিনে-জানে এবং পরকালের মুক্তির লক্ষ্যে এমন কোন ঈমানদার ব্যক্তির পক্ষেই কোন একজন লোককেও ঠাট্টা-বিদ্রূপ অপমান লাঞ্ছিত করতে চাওয়া বা করা, কাউকে তিরষ্কার-মন্দ বলার লক্ষ্যে পরিণত করা এবং দিন-রাত তাকে জ্বালাতন করা কিছুতেই জায়েয হতে পারে না। কেননা এ কাজ যে করে তার মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন আত্মম্ভরিতা-অন্যদের তুলনায় নিজেকে বড় মনে করার হীন মানসিকতা রয়েছে বলে মনে করা যেতে পারে। এ লোক আল্লাহর কাছে ভালত্বের মানদণ্ড কি তা আদৌ জানে না। এ জন্যেই আল্লাহ্ তা’আলা বলেছেনঃ ( আরবি*******************)
কোন লোক অপর কোন লোককে ঠাট্টা-বিদ্রূপ-অপমান করবে না। কেননা তারা তাদের চাইতে উত্তম হতে পারে। তেমনি কোন মেয়ে অপর মেয়েদের ঠাট্টা-বিদ্রূপ অপমান করবে না, কেননা তারাও তাদের তুলনায় ভাল হতে পারে।
বস্তুত আল্লাহর কাছে ভালত্বের মানদণ্ড ঈমান, একনিষ্টতা ও আল্লাহর সাথে ভাল সম্পর্ক- এ নিয়ে গঠিত। আকার-আকৃতি, দেহ-আবয়ব, মান-সম্মান ও ধন-দৌলতের ওপর তা ভিত্তিশীল নয়। হাদীসে বলা হয়েছেঃ ( আরবি*******************)
আল্লহ্ তোমাদের আকার-আকৃতি ও ধনমালের দিকে তাকান না, তার কোন গুরুত্ব দেন না। তিনি দেখেন তোমাদের হৃদয় ও আমলের দিকে- তার কাছে এরই গুরুত্ব রয়েছে।
এমতাবস্থায় কোন পুরুষ কি অপর পুরুষকে এবং কোন নারী কি অপর নারীকে দৈহিক গঠন, আঙ্গিক ত্রুটি-কমতি কিংবা দারিদ্র্য ও অসচ্ছলতার দরুন ঠাট্টা-বিদ্রূপ-অপমান করতে পারে ? করা কি কোনক্রমে জায়েয হতে পারে ?
হাদীসে উদ্ধৃত হয়েছে, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা)-এর নলার কাপড় খুলে গেলে দেখা গেল তা খুবই সরু পাতলা। উপস্থিত কেউ কেউ তা দেখে বিদ্রূপের হাসি হেসে উঠল। তখন নবী করীম (সা) বললেনঃ ( আরবি*******************)
তোমরা ওর হালকা-পাতলা-সরু পায়ের নলা দেখে হাসছ? যার হাতে আমার প্রাণ তাঁর নামের শপথ, এ দুইখানি পা আল্লাহর দাড়ি-পাল্লায় ওহুদ পর্বতের চাইতেও অধিক ভারী।
অপরাধী মুশরিকরা মুমিন মুসলমানকে কি ভাবে ঠাট্টা-বিদ্রূপ-অপমান করত, বিশেষ করে তাদের মধ্যকার বিলাল ও আম্মারের ন্যায় দুর্বল লোকদের, তার বিবরণ কুরআন মজীদে দেয়া হয়েছে। কিয়ামতের দিন পাল্লা কিভাবে উল্টে যাবে এবং আজকের ঠাট্টা-বিদ্রূপ-অপমানকারীরাই যে সেদিন ঠাট্টা-বিদ্রূপের পাত্র হবে, তাও বলে দিয়েছে। বলা হয়েছেঃ ( আরবি*******************)
যারা অপরাধী তারা ঈমানদার লোকদের দেখে ঠাট্টা-বিদ্রূপের হাঁসি হাসত। তাদের কাছে গেলে তারা পরস্পরকে ইঙ্গিত-ইশারা করত। আর যখন নিজেদের ঘরের লোকদের কাছে ফিরে যেত, তখন খুব তৃপ্তি ও সার্থকতা প্রকাশ করত। তাদের দেখতে পেলে তারা বলত, এরা সব পথভ্রষ্ট লোক। অথচ তাদের ওপর এদেরকে রক্ষাকারী করে পাঠান হয়নি। তাই আজকের দিনে ঈমানদার লোকেরা কাফিরদের প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রূপের হাসি হাসবে।
এ আয়াতের প্রথমাংশের কথায়ই মেয়েদের পরস্পরে ঠাট্টা-বিদ্রূপ-অপমান করার নিষেধ শামিল রেয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের সম্পর্কে স্বতন্ত্রভাবে স্পষ্ট ভাষায় বলার প্রয়োজন মনে করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, কোন মেয়েলোক যেন অপর মেয়েলোকদের ঠাট্টা-বিদ্রূপ-অপমান না করে। তার কারণ এই যে, মেয়েদের পরস্পরের এ কাজ খুবই জঘন্য ও বীভৎস চরিত্র ও মন-মানসিকতার পরিচায়ক এবং তাদের মধ্যেই এটা ব্যাপক ও প্রকট লক্ষ্য করা যায়।
দুর্নাম করা, দোষী করা
এ পর্যায়ের দ্বিতীয় নিষিদ্ধ কাজ হচ্ছে অন্য লোকদের দুর্নাম করা, দোষী করা। যে লোক অন্যদের দুর্নাম করে, দোষী করে, সে যেন তাদের তীর বা তরবারির আঘাতে আহত ও জখমি করে। কিন্তু মুখের কথায় আঘাত আরও মারাত্মক। আরবী কবিতায় বলা হয়েছেঃ ( আরবি*******************)
লেজা-বল্লমের ক্ষত তো শুকিয়ে ভাল হেয়ে যায়, কিন্তু মুখের কথার আঘাত কখনই সারে না।
আয়াতে যেভাবে শব্দটি বলা হয়েছে, তা আল্লাহর ওহীর বিশেষত্ব বৈ কি। বলা হয়েছেঃ ( আরবি*******************)-তোমরা নিজেদের আহত, ক্ষত করো না।
আর্থাৎ তোমরা পরস্পরকে আহত ক্ষত-বিক্ষত করো না। এ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, কুরআন মুসলিম সমাজকে ‘এক অখণ্ড ব্যক্তিত্ব’ মনে করে। কেননা তারা সকলেই পরস্পরের জন্যে দায়িত্বশীল, পরিপূরক। এক্ষণে একজন যদি তার ভাইকে আহত করে, তাহলে প্রকৃতপক্ষে সে তার নিজেকেই আহত ও ক্ষত-বিক্ষত করে।
খারাপ উপাধিতে ডাকা
অন্যকে ক্ষত-বিক্ষত করা হারাম হওয়ার সাথে সাথে পরস্পর খারাপ উপাধিতে ডাকাও হারাম। অন্যকে এমন শব্দে বা নামে ডাকা যা তার খুবরাপ লাগে, সে তা অপছন্দ করে। কেননা তাতে তাকে অপমান ও বিদ্রূপ করা হয় এবং ক্ষত-বিক্ষত করা হয়। তার অন্তরে আঘাত দেয়া হয়। কিন্তু কোন মানুষেরই উচিত নয় তার কোন ভাইকে এভাবে কষ্ট দেয়া। এতে করে মানুষের মন-মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। ভ্রাতৃত্বের সীমা লংঘন করা হয়। সাধারণ সৌজন্য ও রুচির পরিপন্থী এ কাজ।
খারাপ ধারণা
ইসলাম চায় মুসলিম সমাজের ব্যক্তিগণ পরস্পরের প্রতি পরিচ্ছন্ন, নির্মল-নির্দোষ মন-মানসিকতা নিয়ে বসবাস করুক। পরস্পরের প্রতি পরম আস্থা ও নির্ভরতা স্থিতিশীল হোক। পরস্পরের প্রতি কোনরূপ সন্দেহ অনাস্থা ও অবিশ্বাস পোষণ না করুক। কেউ কারো প্রতি যেন খারাপ ধারণা না রাখে, মিথ্যা দোষারোপ না করে। এ কারণ পূর্বোদ্ধৃত আয়াতে চতুর্থ নিষিদ্ধ-হারাম কাজ হিসেবে এই কথার উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা ইসলাম কোন অবস্থায়ই মানুষের মান-মর্যাদার ক্ষুণ্ণতা বরদাশত করতে প্রস্তুত নয়। বলা হয়েছেঃ ( আরবি*******************)
হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা লোকদের প্রতি বহু ধরনের ধারণা পোষণ এড়িয়ে চল। কেননা কোন কোন ধারণা গুনাহ হয়ে থাকে। (সূরা হুজরাতঃ ১২)
বলা বাহুল্য, ধারণা বলতে এখানে খারাপ ধারণা পোষণের কথাই বলা হয়েছে।
অতএব কোন মুসলমানেরই তার মুসলিম ভাই সম্পর্কে খারাপ ধারণা পোষণ করা উচিত নয়, যথক্ষণ না অকাট্য কোন প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে।
মানুষ সম্পর্কে মৌলিকভাবেই ধরে নিতে হবে যে, তারা নির্দোষ। খারাপ ধারণার ওয়াসওয়াসা নির্দোষ মানুষকে দোষী সাব্যস্ত করবে, তা কিছুতেই উচিত নয়। নবী করীম (সা) তাই বলেছেনঃ ( আরবি*******************)
লোকদের সম্পর্কে কু-ধারণা থেকে দূরে থাক। কেননা কুধারণা অত্যন্ত মিথ্যা কথা।
একথা ঠিক যে, মানুষ মানবীয় দুর্বলতার কারণে কুধারণা ইত্যাদি থেকে অনেক সময় নিজেকে দূরে রাখতে সমর্থ হয় না। কোন কোন লোক সম্পর্কে তাদের মনে সন্দেহ জেগে উঠে। বিশেষ করে যাদের সাথে সম্পর্ক খারাপ হয়ে গেছে তাদের বিষয়ে। কিন্তু মুসলমান মাত্রেরেই কর্তব্য সেই কু-ধারণার কাছে নতি স্বীকার না করা, মানে তাকে স্থান না দেয়া এবং তার পিছনে ছুটে না বেড়ান। এ পর্যায়েও হাদীস বর্ণিত হয়েছেঃ ( আরবি*******************)
তোমার মনে কু-ধারণার সৃষ্টি হলে তুমি তাকে সত্য মনে করে নিও না।
দোষ খুঁজে বেড়ান
অন্য লোকদের প্রতি অনাস্থা মানুষকে একটা গোপন মানসিক অবস্থার দিকে ঠেলে নেয়। আর তা হচ্ছে কু-ধারণা পোষণ। তখন সে একটা বাহ্যিক দৈহিক তৎপরতায় লিপ্ত হয়। সেটি হচ্ছে দোষ খুঁজে বেড়ান। অথচ ইসলাম মানব মসাজকে এক সাথে অন্তর-বাহির উভয় দিক দেয়ে পরিছন্ন ও নির্মল পরিবেশের মাধ্যে রাখতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।
এ কারণে কু-ধারণা পোষণ করতে নিষেধ করার সাথে সাথে পরের দোষ খুঁজে বেড়ান থেকেও নিষেধ করেছেন। কেননা এ কু-ধারণাই দোষ খুঁজে বেড়ানর মূল কারণ হয়ে থাকে।
বস্তুত প্রতিটি মানুষের একটা সম্মান ও মর্যাদা রয়েছে। তার দোষ খুঁজে বেরিয়ে সম্মান মর্যাদার সে আচরণ ছিন্ন করা এবং তার লুকিয়ে থাকা বিষয়াদি জনসমাজে উন্মুক্ত ও উলঙ্গ করে দেয়া কিছুতেই জায়েয হতে পারে না। কেউ নিজস্বভাবে কোন দোষ বা পাপ কাজেই লিপ্ত থাক না কেন। তা যতক্ষণ গোপন থাকছে, ততক্ষণ কারো উদ্যোগী হয়ে তা প্রকাশ করে দেয়া সম্পূর্ণ অনুচিত ও অবাঞ্ছনীয় কাজ।
হযরত উকবা ইবনে আমের (রা)-এর দরবারী লেখক আবুল হায়সাম বলেন, আমি উকবা ইবনে আমেরকে বললামঃ আমার কিছু সংখ্যক প্রতিবেশী রয়েছে, তারা মদ্য পান করে, আমি পুলিশ ডেকে ওদের ধরিয়ে দিতে চাই। তখন তিনি বললেনঃ না তা করো না। তাদের বুঝাও, উপদেশ দাও, নসীহত কর। বললঃ আমি তো ওদের অনেক নিষেধ করেছি কিন্তু ওরা শুনছে না। এমতাবস্থায় পুলিশ ডেকে ওদের ধরিয়ে দেয়া ছাড়া আর কি করা যেতে পারে? তিনি বললেনঃ না, তোমার জন্যে আফসোস! তুমি তা করতে যেও না। আমি রাসূলে করীম (সা)-কে বলতে শুনেছিঃ ( আরবি*******************)
যে লোক কারো গোপন কথা গোপন রাখল- প্রকাশ করে দিল না, সে যেন কোন জীবন্ত প্রোথিতকে তার কবরে জীবিত করে দিল। (আবূ দাঊদ, নিসারী, ইবনে মাযাহ)
লোকদের গোপন দোষ খুঁজে বেড়ানকে নবী করীম (সা) মুনাফিকদের খাসলাতের মধ্যে গণ্য করেছে। আর মুনাফিক তারা, যারা মুখে বলে ঈমান এনেছি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাদের অন্তর ঈমান আনেনি। নবী করীম (সা) লোকদের সামনেই এ লোকদের কঠোর ভাষায় সমালোচনা করেছেন। হযরত ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী করীম (সা) মিম্বারের ওপর দাঁড়িয়ে উচ্চতর কণ্ঠে ডাক দিয়ে বললেনঃ ( আরবি*******************)
হে সেসব লোক- যারা মুখে ঈমান ও ইসলাম কবুল করেছে, কিন্তু তাদের অন্তর পর্যন্ত ঈমান পৌঁছাতে পারে নি। তোমরা মুসলমানদের কষ্ট দিও না। এবং তদের গোপন দোষ খুঁজে বেড়িও না। কেননা যে লোক তার মুসলিম ভাইয়ের গোপন দোষ খুঁজে বেড়ায়, আল্লাহ্ তার দোষ খুঁজে বেড়াবেন। আর আল্লাহ্ যার গোপন দোষ খুঁজবেন তাকে তিনি লজ্জিত অপমানিত করবেন যদিও সে তার ঘরের কোণে বসে থাকে। (তিরমিযী, ইবনে মাযাহ)
লোকদের মান-মর্যাদার পূর্ণ সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা দানের উদ্দেশ্যেই নবী করীম (সা) কারো ঘরের লোকদের অনুমতি ব্যতিরেকে প্রবেশ করাকে কঠোরভাবে হারাম করে দিয়েছেন। এ জন্যে ঘরের লোকদের তরফ থেকে যদি কোন প্রতিঘাত আসে, তাহলে কোন অপরাধ হবে না বলে জানিয়েছে। বলেছেনঃ ( আরবি*******************)
যে লোক অপর কারো ঘরের ভিতরে উঁকি দিল তাদের অনুমতি ছাড়াই, ঘরের লোকদের জন্যে তার চক্ষু ফুটো করে দেয়া সম্পূর্ণ হালাল হয়ে গেছে।
ঘরের মধ্যে বসে লোকদের বলা কথাবার্তা তাদের অবহিত ও অনুমতি ছাড়া অপর লোকদের শোনা হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। নবী করীম (সা) বলেছেনঃ ( আরবি*******************)
যে লোক অন্য লোকদের কথাবার্তা চুরি করে শুনবে- সেই লোকেরা কিন্তু চায় না যে, তাদের কথা কেউ লকিয়ে থেকে শুনুক- কিয়ামতের দিন তার দুই কানে গলিত সীসা ঢেলে দেয়া হবে। (বুখারী)
কেউ যদি কারো সাথে সাক্ষাত করার উদ্দেশ্যে তার বাড়িতে গমন করে, তখন তার অনুমতি ছাড়া ও সালাম করা ছাড়াই ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়া সম্পর্ণ হারাম। সে জন্যে তাকে প্রথমে সালাম করতে হবে ও প্রবেশের অনুমতি চাইতে হবে। এইটা ওয়াজিব। ইরশাদ হয়েছেঃ ( আরবি*******************)
হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা অন্যদের ঘরে প্রবেশ করবে না যতক্ষণ না অনুমতি চাইবে ও ঘরের লোকদের প্রতি সালাম করবে। তোমাদের জন্যে এটাই কল্যাণকর। সম্ভবত তোমরা মনে রাখবে। সে ঘরে যদি কাউকে না-ই পাও, তাহলে তাতে তোমরা প্রবেশ করবে না, যতক্ষণ না তোমাদের জন্যে পবিত্রতর কর্মনীতি। তোমরা যা কিছু কর সে বিষয়ে আল্লাহ্ পুরাপুরি অবহিত। (সূরা নূর ২৭-২৮)
হাদীসে উদ্ধৃত হয়েছেঃ ( আরবি*******************)
যে লোকই কোন গোপনীয় জিনিস উন্মুক্ত করবে এবং অনুমতি দেয়ার আগেই তার দৃষ্টি নিক্ষেপ করল, তাহলে সে এমন সীমার মধ্যে প্রবেশ করল, যে সীমার মধ্যে প্রবেশ করা তার জন্যে হালাল নয়। (আহমদ, তিরমমিযী)
পরের দোষ খুঁজে বেড়ানো- লুকানো ত্রুটি আতিপাতি করে খুঁজে বের করা সাধারণভাবে সকলের জন্যেই হারাম। শসক-প্রশাসক এবং শাসিত জনগণ সকলের জন্যেই এই নিষেধ। কেউই এ থেকে মুক্ত নয়, কারো জন্যেই তার অনুমতি নেই। হযরত মুআবিয়া (রা) রাসূলে করীম (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেনঃ ( আরবি*******************)
তুমি যদি লোকদের গোপন দোষ তালাশ করে বেড়াও, তাহলে তুমি তাদের বিপর্যস্ত করবে কিংবা বিপর্যয়ের কাছে পৌঁছে দেবে। (আবূ দাউদ, ইবনে মাযাহ)
তিনি আরও বলেছেনঃ ( আরবি*******************)
শসক বা প্রশাসক যখন লোকদের মধ্যে সন্দেহ সংশয়ের কথাবার্তা খুঁজে বেড়াতে শুরু করে, তখন সে তাদের বিপর্যস্ত করে দেয়। (আবূ দাউদ)
গীবত
উপরিউক্ত আয়াত ষষ্ঠ পর্যায়ে যে জিনিস হারাম করে দিয়েছে, তা হচ্ছে গীবত। আয়াতাংশ হচ্ছেঃ ( আরবি*******************)
তোমরা যেন পরস্পরের গীবত করো না। (সূরা হুযরাতঃ ২১)
নবী করীম (সা) সওয়াল-জবাব পন্থায় তাঁর সাহাবীদের ‘গীবত’ শব্দের সংজ্ঞা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি তাদের লক্ষ্য করে বললেনঃ ( আরবি*******************) – তোমরা কি জান, গীবত কাকে বলে?
সাহাবিগণ বললেনঃ আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলই ভাল জানে। তখন তিনি বললেনঃ ( আরবি*******************)
তোমার ভাইয়ের উল্লেখ এমনভাবে করা, যা সে নিজে পছন্দ করে না- তাই হচ্ছে গীবত। জিজ্ঞেস করা হলো, ইয়া রাসূল, আমি যা বলি তা যদি আমার সেই ভাইয়ের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে থেকে থাকে, তাহলেও কি তা বলা গীবত হবে। বললেনঃ তুমি যা বল তা যদি তার মধ্যে থেকেই থাকে, তবেই তো গীবত হবে। আর যদি নাই থাকে, তাহলে তো বহতান- মিথ্যা দোষারোপ হবে। (মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী)
মানুষ পছন্দ করে না- এমন কথা তার জন্য তার অনুপস্থিতিতে বলা- এ পর্যায়ে তার দৈহিক গঠন আকার-আকৃতি, চরিত্র, কাজ-কর্ম, বংশ ও তার সঙ্গে জড়িত সমস্ত বিষয়ই এর অন্তর্ভুক্ত। হযরত আয়েশা (রা) বলেছেনঃ ( আরবি*******************)
আমি রাসূলে করীম (সা)-কে বললামঃ আপনার বেগম সাফিয়ার খাঁটো হওয়াটাই যথেষ্ট। তখন নবী করীম (সা) বললেনঃ তুমি এমন একটা কথা বললে, যদি তা সমুদ্রের পানির সাথ মিলেয়ে দেয়া হয়, তাহলে সে পানির রং বদলে যাবে। (আবূ দাঊদ, তিরমিযী, বায়হাকী)
আসলে গীবত দ্বারা অন্যদের হীন পতিপন্ন করা কুপ্রবৃত্তিরই প্রকাশ ঘটে। তাদের অনুপস্থিতির সুযোগে তাদের মান-সম্মান-মর্যাদাকে ক্ষণ্ণ করার প্রবল ইচ্ছাই কাজ করে। তা গীবতকারীর হীন মন-মানসিকতা, নীচতা ও কুপ্রবৃত্তির পরিচয় দিয়ে দেয়। কেননা তা পিছন থেকে আঘাত হানার শামিল। তা প্রমাণ করে যে, গীবতকারীর নিজের কোন কাজ নেই। সে-ই তো গীবত করার কাজে পটুতা দেখায়। গীবত প্রবণতা সমাজ বিধ্বংসী কার্যক্রম, কেননা যারা গীবত করতে অভ্যস্ত তাদের জিহবার তরবারির আঘাত থেকে খুব কম লোকই রক্ষা পেতে পারে।
এমতাবস্থায় কুরআন মজীদে যদি তার বীভৎস ও জঘন্য রূপ উদঘাটিত করে থাকে এবং এমনভাবে তার চিত্র উপস্থাপিত করে থাকে, যা মানুষের মনে তীব্র ঘৃণার উদ্রেক করে, তাহলে তাতে বিস্ময়ের কোন কারণ নেই। সে চিত্রটি এইঃ ( আরবি*******************)
তোমাদের কেউ যেন অপর কারো গীবত না করে। তোমাদের কেউ কি পছন্দ করে তার মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়া?- তা তোমরা অপন্দ করই।
বস্তুত মানুষ মানুষের গোশত খাওয় আদৌ পছন্দ করতে পারে না। তাহলে নিজ ভাইয়ের গোশত খাওয়া- মৃত ভাইয়ের গোশাত খাওয়া কি করে তার পক্ষে সম্ভব হতে পারে?
নবী করীম (সা) যখনই সুযোগ, ক্ষেত্র ও পরিবেশ পেতেন, গীবতের এই চিত্র তখনই তিনি উদঘাটিত করতেন এবং লোকদের মনে এই বীভৎস ছবি সর্বদা জাগ্রত থাক, তাই তিনি চইতেন।
হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বলেছেনঃ ( আরবি*******************)
আমরা রাসূলে করীম (সা)-এর দরবারে উপস্থিত ছিলাম। এক ব্যক্তি তখন মজলিসের বাইরে চলে গেল। তখন এক ব্যক্তি সে লোকটি সম্পর্কে অপমানকর কথা বলল। তখন নবী করীম (সা) এই ব্যক্তিকে বললেনঃ তুমি খেলাল কর। লোকটি বললঃ আমি কেন খেলাল করব, আমিতো কোন গোশত খাইনি? নবী করীম (সা) বললেনঃ তুমি এইমাত্র তোমান ভইয়ের গোশত খেয়েছ।
হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ ( আরবি*******************)
আমরা নবী করীম (সা)-এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। তখন খুব দুর্গন্ধময় বাতাস প্রবাহিত হলো। নবী করীম (সা) বললেনঃ তোমরা জান, এইটা কিসের বাতাস?...এইটা হচ্ছে মুমিনদের যারা গীবত করে, তাদের বাতাস। (আহমদ)
গীবতের অনুমতি-সীমা
উপরে উদ্ধৃত সব কুরআনের আয়াত ও হাদীসে অকাট্যভাবে প্রমাণ করে যে, ইসলামে ব্যক্তির মর্যাদা অত্যন্ত পবিত্র ও সুরক্ষিত।
কিন্তু ইসলামে বিশেষজ্ঞদের মতে গীবতের কয়েকটি দিক হারাম থেকে ব্যতিক্রম। প্রয়োজনের তাগিদে যেখানে গীবত না করে কোন উপায় থাকে না, তা হচ্ছে এই ব্যতিক্রমের দিক এবং এই ব্যতিক্রমের সুযোগ প্রয়োজনের দরুনই ব্যবহার করা যেতে পারে।
যে মজলুম জালিমের বিরুদ্ধে ফরিয়াদ করে, সে জালিমের এমন সব কথা প্রকাশ করে যা তার খারাপ লাগলেও সে কথাগুলো সবই সত্য এবং তার সে অধিকারও আছে। এই জুলুমের ক্ষেত্রে ফরিয়াদ করার জন্যে কারো বিরুদ্ধে বলার প্রয়োজন দেখা দিলে তা অবশ্যই বলতে হবে। আল্লাহ্ তা’আলা ইরশাদ করেছেনঃ ( আরবি*******************)
আল্লাহ্ ত’আলা খারাপ ধরনের কথা প্রকাশ ও প্রচার করা আদৌ পছন্দ করেন না, তবে যার ওপর জুলুম হয়েছে, তার তা করা স্বতন্ত্র ব্যাপার। আর আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাত। (সূরা আন-নিসাঃ ১৪৮)
এক ব্যক্তি অপর এক নির্দিষ্ট ব্যক্তির সম্পর্কে জানতে চায় এই উদ্দেশ্যে যে, লোকটির ভাল চরিত্র সম্পর্কে জানতে পারলে তার সাথে ব্যবসায়ে শরীক হবে অথবা কেউ তার কন্যা বিয়ে দেবে, প্রস্তাবক ছেলে সম্পর্কে সে জানতে চায়। এ সব ক্ষেত্রে একদিকে থাকে লোকদেরকে সঠিক কথা ও প্রকৃত অবস্থা জানানর দায়িত্ব আর অপরদিকে থাকে অনুপস্থিত ব্যক্তির ইজজত-আবরু রক্ষার কর্তব্য। এ দায়িত্ব ও কর্তব্যের মধ্যে প্রবল বিরোধিতা ও সংঘর্ষ বিদ্যমান। কিন্তু প্রথম দায়িত্ব যেহেতু সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও পবিত্র, সেই কারণে সেটির অগ্রাধিকার অবশ্য স্বীকার করতে হবে। ফাতিমা বিনতে কাইস নবী করীম (সা)-কে তার বিয়ের জন্যে আসা দুটি প্রস্তাব সম্পর্কে অবহিত করে কোনটি গ্রহণ করবেন তার পরামর্শ চাইলেন। তখন তিনি তার একজন সম্পর্কে বললেনঃ এ লোকটি স্ত্রীকে খুব মারধোর করে। সে তার লাঠি কাঁধের ওপর থেকে কখনই নামায় না।
এ ব্যতিক্রমের মধ্যেই রয়েছে অন্যায় ও পাপকে বদলে দেয়ার উদ্দেশ্যে কথা বলা। হাদীস অনুযায়ীই এটা কর্তব্য।
কোন লোকের পরিচিতিই যদি হয় এমন নামে, যা সে নিজে পছন্দ করে না অথচ সেই নাম না বললে তাকে চেনাই যায় না- যেমন আরাজ- ‘ল্যংগরা’, আমাশ (দুর্বল দৃষ্টি শক্তিসম্পন্ন) বা অমুক মেয়ে লোকের পুত্র ইত্যাদি। তাই এ পরিচিতির উদ্দেশ্যেই তা বলতে হবে। সাক্ষী, হাদীস বর্ণনাকারী ও খবরদাতাদের জেরা করা- তাদের চারিত্রিক দোষ-গুণ আলোচনা করাও এ পর্যায়েরই কাজ।
এ পর্যায়ে ‘গীবত’ জায়েয হওয়ার দুটি ভিত্তি রয়েছেঃ
একটি, প্রয়োজন; দ্বিতীয়, নিয়ত- মনোভাব। অনুপস্থিত ব্যক্তি তার অসন্তুষ্টির বিষয়ে উল্লেখ করার প্রয়োজন তীব্র হয়ে দেখা না দেয়া পর্যন্ত এ নিষিদ্ধ ক্ষেত্রে কারোরই পদাচারণা করা উচিত নয়। যদি ইশারা-ইঙ্গিতে বললে প্রয়োজন মিটে যায়, তাহলে সুস্পষ্ট করে বলা থেকে বিরত থাকতে হবে। অথবা নির্দিষ্ট ব্যক্তির কথা না বলে সাধারণ ভাবে কথাটি বলা যেতে পারে। যেমন জিজ্ঞেস করার একটা ধরনঃ এমন ব্যক্তি সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কি, যে এই এই কাজ করে? সেখানে ‘অমুকের পুত্র অমুকে’ বলা উচিত নয়। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মধ্যে আছে এমন বিষয়ে বলতে গেলে শর্ত প্রযোজ্য। কিন্তু তার মধ্যে নেই তা-ই যদি বলা হয়, তাহলে তা হবে সম্পূর্ণ মিথ্যা দোষারোপ এবং তা সম্পূর্ণ হারাম।
নিয়ত, এটাই হচ্ছে এ পর্যায়ে সব ব্যাপারের চূড়ান্ত ফয়সালাকারী ব্যাপার। কি কারণে সে কথা বলছে, তা অন্যদের অপেক্ষা সে নিজেই ভাল জানেন। এ নিয়তের ভিত্তিতেই গীবত সমালোচনা, উপদেশ এবং দোষ প্রচার করা প্রভৃতির মধ্যে পার্থক্য করা সম্ভব। আর এও সত্য যে, মুমিন তার নিজের মনোভাব সম্পর্কে নিজেই খুব কড়াভাবে হিসেব-নিকেশ করতে পারে এবং করেও থাকে।
ইসলামের দৃষ্টিতে এটাও নিশ্চিত কথা যে, গীবত যে শোনে সেও গীবত কার্যে শরীক মনে করতে হবে। আর প্রত্যেকেরই কর্তব্য তার ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার সাহায্য করা, তর পক্ষে কথা বলা। হাদীসে বলা হয়েছেঃ ( আরবি*******************)
যে লোক তার ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার ইজ্জত সংরক্ষণ করল তার দোষ স্খালন করল, তার হক হচ্ছে আল্লাহ তাকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাবেন। (আহমদ)
( আরবি*******************)
যে লোক তার ভাইয়ের ইজ্জত রক্ষা করল এ দুনিয়ায়, আল্লাহ্ তার থেকে কিয়ামতের দিন জাহান্নামকে ফিরিয়ে নেবেন। (তিরমিযী)
যার এরূপ সাহসিকতা নেই, ভাইয়ের মর্যাদাহানির আঘাত থেকে যে তার ভাইকে রক্ষা করতে পারল না, তার অন্ততপক্ষে সে মজলিস ত্যাগ করে চলে যাওয়া এবং সেই লোকদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা কর্তব্য- যতক্ষণ না তারা অন্য কোন কথায় মনোনিবেশ করছে। তা-ও না করলে সে তো আল্লাহর এ বাক্যটির আওতার মধ্যে পড়ে যাবেঃ ( আরবি*******************) – তোমরাও এক্ষণে তাদের মতোই হয়ে গেলে। (সূরা নিসা ১৪০)
চোগলখোরী
গীবতের কথা যখনই বলা হয়, তখনই তার সাথে এমন আর একটি স্বভাবেরও উল্লেখ করা হয়, যা ইসলমের দৃষ্টিতে গীবতের মতোই কঠিনভাবে হারাম। আর তা হেচ্ছে চোগলখোরী। কারো মুখে একজনের বিরুদ্ধে কিছু শুনে তা সে ব্যক্তির কাছে এমনভাবে পৌঁছে দেয়া, যার ফলে দুজনের মধ্যে ঝগড়া-ঝাটি অনুষ্টিত হয় এবং পারস্পরিক মনের পরিছন্নতা দূর হয়ে গিয়ে পংকিলতা ও ময়লার সৃষ্টি হয়। অথবা পূর্ব থেকে থাকা সেই পংকিলতা ও ময়লা আরও অধিক মাত্রায় বৃদ্ধি পেয়ে যায়।
এ হীন ও মারাত্মক ধরনের খাছরতের প্রতিবাদ করে মক্কী সূরাসমূহেই আল্লাহর কথা নাযিল হয়। তাতে বলা হয়েছেঃ ( আরবি*******************)
এমন ব্যক্তির কথা তোমরা মেনে নিও না, যে খুব বেশি কিরা-কসম খায় ও গুরুত্বহীন, যে লোকদের দুঃখ দেয়, অভিশাপ বর্ষণ করে বেড়ায় এবং চোগলখোরী করে ফিরে। (সূরা আল-কালামঃ ১০-১১)
নবী করীম (সা) বলেছেনঃ ( আরবি*******************)
চোগলখোর জান্নাতে যাবে না। (বুখারী, মুসলিম)
এখানে ‘কাত্তাতুন’ শব্দটির অর্থ চোগলখোর। কেউ কেউ বলছেনঃ আসলে চোগলখোর সে, যে কথাবার্তায় মগ্ন একদল লোকের সঙ্গে শামিল থাকে, পরে তাদের বিরুদ্ধে গিয়ে চোগলখোরী করে। আর ‘কাত্তাতুন’ হচ্ছে সে, যে লোকদের অজ্ঞাহসারে তাদের কখাবার্তা শুনে তাদের বিরুদ্ধে বলতে শুরু করে।
নবী করীম (সা) বলেছেনঃ ( আরবি*******************)
আল্লাহর নিকৃষ্টতম বান্দা হচ্ছে তারা, যারা চোগলখোরী করে। বন্ধুদের পরস্পরের মধ্যে বিরোধ ও ফাটলের সৃষ্টি করে এবং নির্দোষ লোকদের দোষ বের করার জন্যে চেষ্টা করতে থাকে। (আহমদ)
পারস্পরিক বিবাদ দূর করে মীমাংসা ও মিলমিশের জন্যে যারা চেষ্টা করে ইসলাম তাদের জন্যে এটা জায়েয বলেছে যে, একজনের সম্পর্কে খারাপতম কথা জানা সত্ত্বেও সে তা প্রকাশ করবে না। উপরন্তু নিজের পক্ষ থেকে এমন কিছু ভাল ভাল কথা বাড়িয়ে বলবে যদিও তা একজন সম্পর্কে অপরজনের কাছ থেকে শুনতে পায়নি।
যারা কোন খারাপ কথা কোথাও শুনতে পায়, আর অমনি তা ষড়যন্ত্রমূলকভাবে বা বিদ্বেষ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে অন্যদের কাছে গিয়ে বলে দেয়, তাদের ওপর ইসলামের তীব্র ক্রোধ ও আক্রোশ। কেননা এরা সমাজে ধ্বংস ও বিপর্যয় সৃষ্টি করার কুমতলবেই তা করে থাকে।
এ ধরনের লোকেরা যতটুকু শুনে ততটুকু মূলধনের ওপরই নির্ভর করে না, সমাজ-বিধ্বংসী মনোবৃত্তি যা শুনেছে তার ওপর নিজেদের পক্ষ থেকে অনেক বাড়িয়ে দিতে এবং মনগড়াভাবে রচনা করে নিতেও কৃণ্ঠিত হয় না। আর তারা যদি ভাল কিছু শুনে তাহলে গোপন রাখে। আর খারাপ কিছু শুনলে তা ব্যাপকভাবে প্রচার করে। আর না শুনলে মিথ্যা বলে।
এক ব্যক্তি হযরত উমর ইবনে আবদুল আজীজের কাছে অপর এক ব্যক্তির পক্ষ থেকে তাকে এমন কিছু শোনাল যা তিনি পছন্দ করেন নি। তখন খলীফা উমর (২য়) বললেনঃ তুমি চাইলে আমি তোমার ব্যাপারটা দেখব। আর তুমি যদি মিথ্যাবাদী হও, তাহলে তুমি কুরআনের এ আয়াতের পর্যায়ে পড়ে গেছঃ ( আরবি*******************)
তোমাদের কাছে কোন ফাসিক ব্যাক্ত এসে যদি কোন সংবাদ দেয়, তাহলে তোমরা তার সত্যতা- যথার্থতা অবশ্যই যাচাই করে দেখবে।
আর তুমে যদি সত্যবাদী হও, তাহলে তুমি এ আয়াতের আওতার মধ্যে গণ্যঃ ( আরবি*******************) আর তুমি যদি চাও, তাহলে তোমাকে আমরা মাফ করে দেব। লোকটি বললঃ ‘হে আমীরুল মুমিনিন, ক্ষমা করে দিন। আমি এ ধরনের কাজ আর করব না।’
মান-সম্মান সংরক্ষণ
ইসলাম তার উচ্চতর মানের শিক্ষার দ্বারা মানুষের মান-সম্মান ও মর্যাদা সংরক্ষণের ওপর কতখানি গুরুত্ব দিয়েুছে, তা আমরা দেখেছি। মানুষের মর্যাদা সংরক্ষণের ব্যাপারটি তার পবিত্রতা বিধানের সীমানা পর্যন্ত পৌঁছে গেছে, তাও লক্ষণীয়। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) একদা কাবা ঘরের দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলেনঃ ( আরবি*******************)
হে কাবা! তোমার বিরাট মর্যাদা, তোমার মর্যাদার বিরাটত্ব বিষয়ে আর কি বলব। কিন্তু মুমিন লোকের মর্যাদা তোমার চাইতেও অনেক উচ্চ ও বড়। আর মুমিনের মর্যাদা প্রতিফলিত হয় তার ইজ্জতের, রক্তের ও ধন-মালের মধ্য দিয়ে।
বিদায় হজ্জের ভাষণে নবী করীম (সা) বিরাট ইসলামী জনতাকে সম্বোধন করে বলেছিলেনঃ ( আরবি*******************)
জেনে রাখো তোমাদের ধন-মাল, তোমাদের ইজ্জত-আবরু এবং তোমাদের রক্ত পরস্পরের ওপর হারাম-সম্মানার্হ, তোমাদের আজকের দিনের মর্যাদার মতো- তোমাদের এ মাসে তোমাদের এ নগরে।
ব্যক্তির ইজ্জত-আবরুও ইসলাম রক্ষা করেছে তার অনুপস্থিতিতে তার সম্পর্কে এমন কথা বলা নিষেধ করে যা সত্য অথচ সে তা অপছন্দ করে। তাহলে যে-কথা মনগড়া ভিত্তিহীন, তা বলার সুযোগ কি করে থাকতে পারে? যদি তা বলা হয়, তাহলে তো অতি বড় পাকা অপরাধ ও গুনাহ হবে। হাদীসে বলা হয়েছেঃ ( আরবি*******************)
যে লোক কারো সম্পর্কে এমন কথা বলল- যা তার মধ্যে নেই- শুধু এ উদ্দেশ্যে যে, তাকে দোষী করবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাকে জাহান্নামে বন্দী করে রাখবেন, যতক্ষণ না তার বলা কথার সত্যতা সে প্রমাণিত করে দেবে। (তাবারানী)
হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা) তাঁর সাহাবিগণকে বললেনঃ ( আরবি*******************)
তোমরা কি জান, আল্লাহ্ কাছে সবচেয়ে বড় সুদ কি? সাহাবিগণ বললেনঃ আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলই জানেন। বললেনঃ সবচেয়ে বড় সুদ আল্লাহর কাছে মুসলমানদের ইজ্জত নষ্ট করতে চাওয়। অতঃপর তিনি কুরআনের আয়াত পাঠ করলেন, যার আর্থঃ যারা মুমিন পুরুষ ও মেয়েলোকদের তাদের নিরপরাধ হওয়া সত্ত্বেও কষ্ট ও পীড়ন দেয়, তারা মিথ্যা দোষারোপ ও সুস্পষ্ট গুনাহের অভিশপ নিজেদের মাথায় তুলে নেয়। (সূরা আহযাবঃ ৫৮)
এ পর্যায়ে সবচাইতে বড় গুনাহ হচ্ছে মনুষের ইজ্জত আবরুর ওপর আক্রমণ চালানো। যেমন পবিত্র চরিত্রা ঈমানদার মুমিন মহিলদের ওপর চরিত্রহীন কাজের দোষারোপ করা। কেননা এতে তাদের সুনাম সুখ্যাতি, তাদের বংশ ও পরিবারের মান-মর্যাদার যেমন ক্ষতি হওয়ার আশংকা, তেমনি তাদের ভবিষ্যতের জন্যেও বিপদ ঘনিয়ে আসতে পারে। উপরন্তু এরূপ করে মুমিনদের সমাজে নির্লজ্জতা ও চরিত্রহীনতার ব্যাপক প্রচার সাধনের প্রবণতাও দেখতে পাওয়া যায়।
এ কারণে নবী করীম (সা) এ কাজটিকে সাতটি ধ্বংসাত্মক কবীরা গুনাহের মধ্যে গণ্য করেছেন এবং কুরআন মজীদ এ কাজের দরুন কঠোর ভাষায় নির্মম পরিণতির ওয়াদা করেছে। বলা হয়েছেঃ ( আরবি*******************)
যেসব লোক মুমিন অসতর্ক পবিত্র চরিত্র সম্পন্না মহিলাদের ওপর চারিত্রিক দোষারোপ করে, দুনিয়া ও পরকালে তাদের ওপর অভিসম্পাত এবং তাদের জন্যে বড় আযাব রয়েছে। সেদিন তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে তাদের মুখ, হাত ও পা, তারা যা যা করেছে সে সম্পর্কে। এ দিন আল্লাহ্ তাদের সত্য প্রতিফলটা পূর্ণ করে দেবেন এবং তারা জানতে পারবে যে, আল্লাহই হচ্ছেন মহাসত্য।
আরও বলা হয়েছেঃ ( আরবি*******************)
যেসব লোক মুমিনদের সমাজে নির্লজ্জতা ও পাপ কাজের ব্যাপক প্রচলন প্রসারতা ঘটাতে ভালবাসে, তাদের জন্যে আযাব দুনিয়ায় ও আখিরাতে- সর্বত্র। আল্লাহই জানেন, তোমরা জান না। (সূরা আন-নূরঃ ১৯)
রক্তের মর্যাদা
ইসলাম মানব জীবনকে সর্বাধিক সম্মানার্হ ও মর্যাদাবান বানিয়েছে। মানবাত্মার পবিত্রতার কথা ঘোষণা করেছে। আর তার ওপর হস্তক্ষেপকে আল্লাহর কাছে কুফরের পর সবচেয়ে বড় গুনাহ রূপে চিণ্হিত করেছে। কুরআন মজীদে ঘোষণা করেছেঃ ( আরবি*******************)
কোনরূপ হত্যার বা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টির অপরাধ ছাড়াই যে লোক একজন মানুষকে হত্যা করে, সে যেন সমস্ত মনুষকে হত্যা হরার অপরাধ করল। তা এ জন্যে যে, ইসলামের দৃষ্টিতে সমস্ত মানুষ একই পরিবারভুক্ত। এমতাবস্থায় তাদের একজনকে হত্যা করা হলে- সীমালংঘন করা হলে সমস্ত মানব-প্রজাতির ওপরই তার আঘাত পড়ে। তার কুফল সকলেই ওপর প্রবর্তিত হয়।
কিন্তু নিহত ব্যক্তি যদি মুমিন হয় তাহলে হারাম হওয়ার ব্যাপারটি অধিকতর কঠিন ও তীব্র হয়ে দাঁড়ায়। কুরআন মজীদে এজন্যে বলা হয়েছেঃ ( আরবি*******************)
যে লোক ইচ্ছা করে কোন মুমিন ব্যক্তিকে হত্যা করবে, তার প্রতিফল হচ্ছে জাহান্নাম। তাতে সে চিরদিন থাকবে। আল্লাহ্ তার ওপর ক্রুদ্ধ হবেন, তার ওপর অভিশাপ বর্ষণ করবেন এবং তার জন্যে বড় আযাব প্রস্তুত করে রাখবেন।
রাসূলে করীম (সা) বলেছেনঃ ( আরবি*******************)
আল্লহর কাছে একজন মুসলমানের নিহত হওয়ার তুলনায় সারা দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাওয়াও অনেক হালকা ব্যাপার। (মুসলিম, নিসায়ী, তিরমিযী)
বলেছেনঃ ( আরবি*******************)
মুমিন দ্বীনের দিক দিয়ে প্রশস্ততার মধ্যে অবস্থান করে যতক্ষণ না হারাম নর হত্যার অপরাধ করে।
বলেছেনঃ ( আরবি*******************)
আল্লাহ্ তা’আলা সম্ভবত সমস্ত গুনহই মাফ করে দেবেন। তবে যে লোক মুশরিক অবস্থায় মরেছে অথবা কোন মুমিন ব্যক্তিকে ইচ্ছা করে হত্যা করেছে তাকে নয়।
এ সব আয়াত ও হাদীসের ভিত্তিতে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) মনে করেছেন যে, হত্যাকারীর তওবা কবুল হবে না। অন্য কথায় তিনি মনে করেছেন, তওবা কবুলের জন্যে শর্ত হচ্ছে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের হক ফিরিয়ে দেয়া কিংবা তাকে সন্তুষ্ট কারা। কিন্তু ব্যক্তির হক কি করে ফিরিয়ে দেয়া যেতে পারে কিংবা তাকে সন্তুষ্টই বা করা যেতে পারে কিভাবে ?
অন্যরা বলেছেন, খালেস তওবা অবশ্যই কবুল হবে। এ ধরনের তওবা শিরকের গুনাহ পর্যন্ত মাফ করিয়ে দেয়। তাহলে তার চাইতে কম মাত্রার গুনাহ কেন তওবায় মাফ হবে না ?
আল্লাহ্ তা’আলা তো বলেছেনঃ ( আরবি*******************)
যেসব লোক আল্লাহর সঙ্গে দ্বিতীয় ইলাহ্ ডাকে না, কোন মানুষকে বিনা কারণে হত্যা করে না এবং জ্বেনা করে না- যে লোক এই এই কাজ করে সে তার গুনাহের বদলা পাবে। কিয়ামতের দিন তার আযাব দ্বিগুণ বাড়িয়ে দেয়া হবে এবং তার মধ্যে অপমানিত অবস্থায় চির দিন থাকবে। তবে যে লোক তাওবা করবে, ঈমান আনবে এবং নেক আমল করবে, আল্লাহ্ তাদের খারাপ কাজগুলোকে ভাল ও নেক কাজে পরিবর্তিত করে দেবেন। আর আল্লাহ্ ক্ষমাশীল দয়াবান। (সূরা আল-ফুরক্বানঃ ৬৮-৭০)
হন্তা ও নিহত উভয়েই জাহান্নামী
নবী করীম (সা) মুসলিমদের সাথে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে লিপ্ত হওয়াকে কুফরির একটা দুয়ার বলে ঘোষণা করেছেন। এটা জাহিলিয়াত যুগের কাজ বলে অভিহিত করেছেন। কেননা তখনকার লোকেরা যুদ্ধে সব সময় লিপ্ত থাকত এবং একটি উষ্ট্রী বা ঘোড়ার কারণে তারা রক্তের বন্যা প্রবাহিত করতেও দ্বিধা করত না। নবী করীম (সা) বলেছেনঃ ( আরবি*******************)
মুসলমানকে গাল দেয়া ফাসিকী কাজ এবং তার সাথে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া সুস্পষ্ট কুফরি। (বুখারী, মুসলিম)
নবী করীম (সা)-এর আর একটি কথাঃ ( আরবি*******************)
আমার চলে যাওয়ার পর তোমরা পশ্চাদপসরণ করে কাফির হয়ে যেও না ও পরস্পরের কল্লা কাটতে শুরু করে দিও না। (বুখারী, মুসলিম)
অপর এক হাদীসে বলা হয়েছেঃ দুজন মুসলমানের একজন যখন তার ভাইর ওপর অস্ত্র ধারণ করে, তখন তারা দুজনই জাহান্নামের কিনারে উপস্থিত হয়। অতঃপর একজন যখন অপরজনকে হত্যা করে, তখন দুজনই জাহান্নামে যায়। প্রশ্ন করা হলো হে রাসূল, হত্যাকারীর জাহান্নামে যাওয়া তো বোধগম্য, কিন্তু নিহত ব্যক্তি কেন জাহান্নামে যাবে? বললেনঃ ( আরবি*******************)
সেও তো তার সঙ্গীকে হত্যা করতে চেয়েছিল। (বুখারী, মুসলিম)
এ কারণে নবী করীম (সা) এমন সমস্ত কাজ করতে নিষেধ করেছেন, যার পরিণতি হত্যা বা রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। অস্ত্রের দ্বারা ইঙ্গিত করাও এ পর্যায়ে পড়ে। তিনি বলেছেনঃ ( আরবি*******************)
তোমাদের কেউ যেন তার ভাইর প্রতি অস্ত্রের দ্বারা ইশারা না করে, কেননা শয়তান কখন তার হাত থেকে অস্ত্র কেড়ে নেবে ও সে জাহান্নামের গর্তে পড়ে যাবে, তা সে হয়ত টেরও পাবে না। (বুখারী, মুসলিম)
বলেছেনঃ ( আরবি*******************)
যেলোক তার ভাইয়ের প্রতি কোন অস্ত্র দ্বারা ইশারা করে তখন ফেরেশতা তার ওপর অভিশাপ করে, যতক্ষণ না সে তা থেকে বিরত হয়, যদিও তার আপন ভাই-ই হোক না কেন। (মুসলিম)
তিনি আরও বলেছেঃ ( আরবি*******************)
কোন মুসলমানের জন্যে জায়েয নয় আর একজন মুসলমানকে ভয় দেখান।
গুনাহ কেবলমাত্র হত্যাকারী পর্যন্তই সীমিত হয়ে থাকে না। বরং তাতে যে লোক কোনরূপ কথা বা কাজ দ্বারা শরীক হয়, সেও এ হত্যা পাপের অংশীদার হয়। তার এই অংশ গ্রহণের মাত্রা অনুযায়ীই আল্লাহর ক্রোধ রোষ ও অসন্তোষ তার ওপর পড়ে। এমন কি হত্যাকাণ্ডের অকুস্থলে যে লোক উপস্থিত থেকেও নিষ্ক্রিয় থাকবে, সেও এই পাপে শরীক হবে। হাদীসে বলা হয়েছেঃ ( আরবি*******************)
যেখানে কোন লোককে বিনা কারণে জুলুম হিসেবে হত্যা করা হয়, তথায় যেন কেউ না দাঁড়ায়। কেননা এ হত্যাকাণ্ডে যে লোক উপস্থিত থাকবে ও তাকে রক্ষা করতে চেষ্টা করবে না, তার ওপরও অভিশাপ অবতীর্ণ হবে।
চুক্তি সম্পন্ন ও যিম্মী ব্যক্তির রক্ত মর্যাদা
এসব আয়াত ও হাদীসে মুসলমানকে হত্যা ও মুসলমানের সাথে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া থেকে সাবধান করা হয়েছে। এটা শরীয়তেরই বিধান মুসলিম সমাজে বসবাসকারী মুসলমানদের জন্যে এ পথ-নির্দেশ। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, অমুসলিমের রক্ত বুঝি হালাল! আসলে মানুষ মাত্রেরই রক্ত অবশ্য রক্ষণীয়। মানুষ হিসেবেই তাকে বাঁচাতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত কোন অমুসলিম মুসলমানদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত না হবে, তাকে হত্যা করা যাবে না। হ্যাঁ যদি মুসলমানদের বিরুদ্ধে অমুসলিম যুদ্ধ ঘোষণা করে, তাহলে তখন তার রক্তপাত করা যেতে পারে। আর সেই অমুসলিম যদি মুসলিম রাষ্ট্রের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয় কিংবা হয় যিম্মী, তাহলে রক্তের নিরাপত্তা অবশ্যম্ভাবী। মুসলিমানের পক্ষে সীমালংঘন করা কিছুতেই হালাল হবে না। এ সম্পর্কে নবী করীম (সা)-এর কথা হচ্ছেঃ ( আরবি*******************)
যে লোক কোন চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তিকে হত্যা করবে, সে জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না। অথচ জান্নাতের সুঘ্রাণ তো চল্লিশ চছর পথের দূরত্ব থেকেও পাওয়া যায়।
অপর বর্ণনায় বলা হয়েছেঃ ( আরবি*******************)
যে লোক কোন যিম্মীকে হত্যা করবে, সে জান্নাতের সুঘ্রাণ পাবে না।
রক্তের মর্যাদা কখন থাকে না
আল্লাহ্ তা’আলা ইরশাদ করেছেনঃ ( আরবি*******************)
তোমরা মানুষকে হত্যা করবে না, যাকে আল্লাহ্ হারাম করেছেন। তবে সত্যতা সহকারে হত্যা করার কথা স্বতন্ত্র। (সূরা আন-আমঃ১৫১)
এখানে যে সত্যতার কথা বলা হয়েছে। যার কারণে নর হত্যা করা যায়, তা হচ্ছে কোন অপরাধের দণ্ডস্বরূপ হত্যা করা। আর সেই অপরাধ তিনটিঃ
১. জুলুম করে হত্যা করা। যে লোকের হত্যাকাণ্ডের অপরাধ প্রমাণিত হবে, তার কিসাস করা ওয়াজিব এবং সেই কিসাস হচ্ছে, হত্যার দণ্ড স্বরূপ হত্যাকারীকে হত্যা করা। অর্থাৎ জানের বদলে জান। কুরআনে বলা হয়েছেঃ ( আরবি*******************)
হত্যার দণ্ডস্বরূপ হত্যা করাই তোমাদের জন্যে জীবন নিহিত।
২. প্রকাশ্যভাবে জ্বেনা করা এমনভাবে যে, চারজন ভাললোক তা নিজেদের চোখে প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে সাক্ষ্যও দেবে। তবে শর্ত এই যে, এ লোকটি হালাল পদ্ধতির বিয়ে সম্পর্কে ওয়াকিফহাল থাকতে হবে। আর সাক্ষী না পাওয়া যাওয়া সত্ত্বেও অপরাধী নিজেই যদি বিচারকের সম্মুখে নিজের অপরাধের অন্তত বারবার স্বীকারোক্তি করে তাতেও অপরাধ প্রমাণিত হবে ও সে অনুযায়ী দন্ড দেয়া হবে।
৩. ইসলাম কবুল করার পর দ্বীন-ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেও শাস্তিস্বরূপ তাকে হত্যা করা যাবে। মুসলিম জাতির বিরুদ্ধে তার এ বিদ্রোহ যখন একটা চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াবে, তখনই এ অবস্থা দেখা দেবে। ইসলাম তো কাউকেই জবরদস্তি বধ্য করে না ইসলাম কবুল করার জন্যে। কিন্তু দ্বীন-ইসলাম নিয়ে কেউ খেলা করেবে- তা কবুল করবে, আবার তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে, ইসলাম তা বরদাস্ত করতে পারে না। ইয়াহূদীরা এরূপ শরু করেছিল। কুরআন মজীদে বলা হয়েছে, তারা তাদের লোকদের বলতঃ ( আরবি*******************)
সকাল বেলা তোমরা ঈমান গ্রহণ কর সেই দ্বীনের প্রতি যা মুসলমানদের প্রতি নাযিল হয়েছে এবং দীনের শেষে তার প্রতি কুফরি কর। সম্ভবতঃ তা দেখে এ লোকেরা সে দ্বীন থেকে ফিরে যাবে। (সূরা আলে-ইমরানঃ ৭২)
কারো রক্তপাত হালাল ও মুবাহ হওয়ার জন্যে নবী করীম (সা) এ তিনটি ভিত্তিকেই সীমিত করে দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেনঃ ( আরবি*******************)
মুসলমানের রক্তপাত করা হালাল নয় এ তিনটি কারণ ছাড়া (১) জানের বদলে জান লওয়া (২) বিবাহিত ব্যক্তি জ্বিনাকার হলে এবং (৩) যে লোক দ্বীন-ইসলাম ত্যাগ করে মুসলিম জামায়াত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে চলে যায়।
কিন্তু এ তিনটি অপরাধের দণ্ড হিসেবে মুসলমানের রক্তপাত করা কেবল শসনকর্তা বা প্রশাসকের পক্ষেই জায়েয ও মুবাহ। ব্যক্তিদের পক্ষে নিজস্বভাবে এ দণ্ড দানের কাজ করা আদৌ জায়েয নয়। কেননা তা হলে শাসন-শৃঙ্খলা বলতে কিছুই থাকবে না। চরম অরাজগতা দেখা দেবে। সমাজে প্রত্যেক ব্যক্তিই তখন নিজস্বভাবে বিচারক ও দণ্ডমুণ্ডের মালিক হয়ে বসবে। ইচ্ছাপূর্বক নরহত্যার ক্ষেত্রে কিসাস করা ওয়াজিব। তবে ইসলাম নিহতের উত্তরাধিকারীদের এ অধিকার দিয়েছে যে, প্রশাসক কর্তৃপক্ষ উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও তারা নিজেদের হাতে কিসাস গ্রহণ করতে পারে। তাতে তাদের মনের দুঃখ ক্ষোভ ও আক্রোশ মিটবে, প্রতিশোধ গ্রহণের স্পৃহা চারিতার্থ এবং আল্লাহর এ কথারও বাস্তবায়ন হবেঃ ( আরবি*******************)
যে লোক অন্যায়ভাবে অকারণ নিহত হবে, তার উত্তরাধিকারীদের জন্যে আমরা (কিসাসুল ওয়ার) এ কর্তৃত্ব দিয়েছি, কিন্তু সে হত্যার কাজে সীমালংঘন করা যাবে না। সে অবশ্যই সাহায্য প্রাপ্ত হবে।
আত্মহত্যা
হত্যা অপরাধ পর্যায়ে যে বিধান এসেছে ব্যক্তির আত্মহত্যার ক্ষেত্রে তা পুরোপুরি প্রযোজ্য, যেমন অন্যকে হত্যা করার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য । কাজেই যে লোক আত্মহত্যা করবে তা যার সাহায্যেই করুক না কেন, সে এমন একটা নরহত্যা ঘটালো যা আল্লহ্ তা’আলা বিনা কারণে অন্যায়ভাবে হত্যা করাকে হারাম করে দিয়েছেন।
বস্তুত কোন মানুষের জীবনই তার নিজের মালিকানাভুক্ত নয়। কেননা সে নিজেকে সৃষ্টি করেনি। তার দেহের একটা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বা একটা জীব-কোষ পর্যন্তও সে নিজে বানায়নি। তার জীবন ও প্রাণ তার কাছে একটা আমানত, আল্লাহই তার কাছে এ আমানত অর্পণ করেছেন। অতএব তার ওপর কোনরূপ হস্তক্ষেপ করার কোন অধিকারই তার থাকতে পারে না। তাহলে সে তা হত্যা করতে পারে কিভাবে? এ জীবন থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্যে কোন নিজস্ব উদ্যোগ নিশ্চয়ই অপরাধ হবে। আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেছেনঃ ( আরবি*******************)
তোমরা নিজেদেরকে নিজেরাই হত্যা করো না। কেননা আল্লাহ্ তো তোমাদের প্রতি অতীব দয়াবান। (সূরা আন-নিসাঃ ২৯)
ইসলাম চায়, মুসলমানরা জীবনের কঠোর কঠিন বাস্তবতার মুকাবিলা করায় অত্যন্ত সাহসী, দুর্বিনীতি ও অনমনীয় হবে। জীবন থেকে পলায়ন করার কোন কেন অধিকার কোন অবস্থায়ই কাউকে দেয়া হয়নি। বিপদ দেখলেই বা কোন সংকট ও সমস্যা দেখা দিলেই জীবনের এ পরিচ্ছেদটি খুলে ফেলে পালাতে চেষ্টা করবে, কোন আশায় ব্যর্থ মনোরথ হয়ে জীবনকেই অস্বীকার করবে, এ অধিকার কারো থাকতে পারে না। মুমিনকে তো জিহাদ-প্রাণপণ চেষ্টা সাধনা করার উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে, অকর্মন্য হয়ে বসে থাকার জন্যে নয়। সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হওয়াই তার কর্তব্য, পলায়ন বা পশ্চাদপসরণ তার জন্যে অশোভন। তার ঈমান ও চরিত্রই তাকে জীবনের ক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যেতে ও নিজেকে সরিয়ে নিতে অস্বীকৃতি জানায়। তার কাছে এমন হাতিয়ার রয়েছে যা কখনও পুরাতন হয় না, সম্পদের এমন অফুরন্ত ভাণ্ডার রয়েছে যা কখনই নিঃশেষ হবে না। আর তা হচ্ছে ঈমানের হাতিয়ার, যা খুবই দৃঢ় ও মযবুত এবং সে ভাণ্ডার হচ্ছে অনমনীয় নৈতিকতার ভাণ্ডার।
যে লোক আত্মহত্যার এ জঘন্য অপরাধ করতে অগ্রসর হবে, সে আল্লাহ্ তা’আলার রহমত থেকে বঞ্চিত হবে ও জাহান্নামে পড়ে আল্লাহর তীব্র রোষ ও অসন্তোষের শিকার হবে বলে নবী করীম (সা) আগে থেকেই হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন। তিনি বলেছেনঃ ( আরবি*******************)
তোমাদের পূর্বে চলে যাওয়া লোকদের মধ্যে এক ব্যক্তি ছিল, সে আহত হয়ে গেল আর সেজন্যে সে ছটফট্ করতে শুরু করে দিল। এ অবস্থায় সে ছুরি হাতে নিয়ে নিজেই নিজের হাত কেটে ফেলল। তাতে এত বেশি রক্ত ঝরল যে, তাতে তার মৃত্যু সঙ্ঘটিত হল। আল্লাহ্ তা’আলা এ ব্যক্তি সম্পর্কে বলেছেনঃ আমার এ বান্দা নিজের ব্যাপারে খুব তাড়াহুড়া করে ফেলেছে। এ কারণে আমি তার প্রতি জান্নাত হারাম করে দিয়েছি। (বুখারী, মুসলিম)
জখমের কষ্ট সয্য করতে না পেরে নিজের হত্যাকাণ্ড নিজেই ঘটিয়েছে বেলে তার ওপর জান্নাত হারাম হয়ে গেল। এ যখন অবস্থা, তখন যারা নিজেদের ব্যবসায় সামান্য ক্ষয়-ক্ষতি, চাকুরীতে উন্নতি না হওয়া বা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে না পারা, অথবা আশায় ভঙ্গ হওয়ার দরুন আত্মহত্যা করে তাদের ব্যাপার কত কঠিন এবং আল্লাহর কাছে কতটা অমার্জনীয় হবে, তা সহজেই বোধগম্য হতে পারে। দুর্বল মনোভাবের লোকদের এ হুঁশিয়ারী শুনে নেয়া কর্তব্য, যা নবী করীম (সা)-এর হাদীসে বলা হয়েছেঃ ( আরবি*******************)
যে লোক নিজেকে পর্বতের ওপর থেকে ফেলে দিয়ে আত্মহত্যা করল, সে জাহান্নামের আগুনে চির দিনই পড়ে থাকবে- কখনই তা থেকে নিষ্কৃতি পাবে না। যে লোক বিষ পান করে আত্মহত্যা করল, সে জাহান্নামের আগুনে চিরকালই নিজ হাতে বিষ পান করতে থাকবে। আর যে লোক কোন লৌহাস্ত্র দ্বারা আত্মহত্যা করল, সে জাহান্নামে চিরদিন চিরকাল ধরে লৌহের সেই জিনিসটি দ্বারা নিজেকে আঘাত দিতে থাকবে। (বুখারী, মুসলিম)
ধন-মালের মর্যাদা
মুসলমানের পক্ষে হালাল পথে ও পন্থায় ধন-মাল উপার্জন করা ও সঞ্চয় করা এবং শরীয়তসম্মত উপায়ে তার পরিমাণ বৃদ্ধি করা কোন দুষণীয় কাজ নয়। অন্যান্য ধর্মগ্রন্থে যেখানে বলা হয়েছেঃ ধনী লোক আসমানী-সাম্রাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে না যতক্ষণ না উষ্ট্র সুঁচের ছিদ্রের মধ্যে প্রবেশ করবে, সেখানে ইসলাম ঘোঘণা করেছেঃ ( আরবি*******************)
ইসলাম হালাল ধন-মালের ওপর ব্যক্তির ব্যক্তিগত মালিকানা জায়েয বলে ঘোষণা করেছে। তাই শরীয়তী আইনের সমর্থনে ও নৈতিক পথ নির্ধারণের সাহায্যে তার ওপর সীমালংঘনকারীদের হস্তক্ষেপ প্রতিরোধ করেছে এবং অপহরণ, চুরি বা ডাকাতি করাকে হারাম করে দিয়েছে।
ধন-মালের এই মর্যাদা, রক্তের মর্যাদা ও মান সম্মানের মর্যাদার কথা নবী করীম (সা) এক সাথে উল্লেখ করেছেন এবং চৌর্যবৃত্তিকে ঈমানের পরিপন্থী বলে ঘোষণা করেছেন। বলেছেনঃ ( আরবি*******************)
চোর যখন চুরি করে তখন সে ঈমানদরি থাকে না।
আল্লাহ্ তা’আলা বলেছেনঃ ( আরবি*******************)
পুরুষ চোর ও মেয়েলোক চোরের হাত কেটে দাও তাদের কাজের প্রতিফলস্বরূপ এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রবর্তিত শাস্তিস্বরূপ। আর আল্লাহ্ দুর্জয়-শক্তিমান মহাবিজ্ঞানী। (সূরা মায়িদাঃ ৩৮)
নবী করীম (সা) বলেছেনঃ ( আরবি*******************)
কারো সন্তুষ্টি ভিত্তিক অনুমতি ছাড়া তার লাঠিখানি নেয়াও মুসলমানের জায়েয নয়।
মুসলমানের ধন-মাল মুসলমানের কাছে অত্যন্ত সম্মানার্হ এবং তা অন্যায়ভাবে গ্রহণ করা সম্পূর্ণ হারাম, এ তীব্রতা বোঝাবার উদ্দেশ্যেই নবী করীম (সা) এরূপ কথা বলেছেন। আল্লাহ্ তা’আলা আরও বলেছেনঃ ( আরবি*******************)
হে ঈমানদারা, তোমরা অন্যায়ভাবে পরস্পরের ধন-মাল ভক্ষণ করো না। তবে তোমাদের পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে ব্যবসায়ের মুনাফা হলে তাতে কোন দোষ নেই। (সূরা আন-নিসাঃ ২৯)
ঘুষ হারাম
বাতিল উপায়ে ও অন্যায়ভাবে লোকদের ধনমাল ভক্ষণ করার একটি পস্থা হচ্ছে ‘ঘুষ’। কেননা প্রভাব ও কর্তত্বসম্পন্ন বা সাধারণ দায়িত্বশীল ব্যক্তিকে এ উদ্দেশ্যে ধনমাল দেয়া যে, সে তার পক্ষে রায় দেবে, তার প্রতিপক্ষের ওপর তাকে জিতিয়ে দেবে কিংবা তাকে কোন কাজ দেবে বা তার শত্রুর কাজকে বিলম্বিত করে দেবে প্রভৃতি উদ্দেশ্যে, তা-ই ঘুষ।
শাসক-প্রশাসক বা তার সহকারীদের জন্যে ঘুষের পথ অবলম্বন করাকে ইসলাম চিরতরে হারাম করে দিয়েছে। তাদের জন্যে তা দেয়া হলে তা কবুল করা বা দাতা-গ্রহীতার মধ্যে মাধ্যম হওয়া- এ সবই হারাম। আল্লাহ্ তা’আলা বলেছেলঃ ( আরবি*******************)
তোমরা তোমাদের ধনমাল পরস্পরে বাতিল পন্থায় ভক্ষণ করো না, না প্রশাসকদের সামনে তা এ উদ্দেশ্যে পেশ কর যে, লোকদের ধন-মালের একাংশ তোমরা নিজেরা ভক্ষণ করবে পরের হক নষ্ট করে এবং জেনে-শুনে।
নবী করীম (সা) বলেছেনঃ ( আরবি*******************)
সরকারী ও রাষ্টীয় ব্যপারাদিতে যে ঘুষ দেয় এবং যে ঘুষ খায়- এ উভয় ব্যক্তির ওপরই আল্লাহর অভিশাপ। (আহমদ)
হযরত সওবান (রা) বলেছেনঃ ( আরবি*******************)
ঘুষদাতা, ঘুষ গ্রহীতা এবং উভয়ের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনকারী- এ সকলেরই ওপর রাসূলে করীম (সা) অভিশাপ বর্ষণ করেছেন। (আহমদ, হাকেম)
ঘুষ গ্রহণকারী যদি কারো ওপর জুলুম করার উদ্দেশ্যে ঘুষ নেয়, তাহলে তার অপরাধের মাত্রা আরও অনেক গুণ বৃদ্ধি পেয়ে যায়। আর যদি সুবিচার করার মানসে এ ঘুষ গ্রহণ করে, তাহলে সুবিচার করা তো তার দায়িত্ব, সেজন্যে কোনরূপ ধনমাল গ্রহণের কোন অধিকার থাকতে পারে না।
রাসূলে করীম (সা) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা)-কে ইয়াহূদীদের কাছে প্রেরণ করেন এ দায়িত্ব দিয়ে যে, তাদের খেজুর ফসলের খারাজ কত টাকা হয় তার পরিমাণ তিনি নির্ধারণ করবেন। তখন তারা তাঁর সামনে ঘুষ স্বরূপ কিছু ধনমাল পেশ করে। হযরত ইবনে রাওয়াহা তা দেখে তাদের বললেন, তোমরা যে ঘুষ পেশ করেছ, তা তো হারাম। আমরা তা কিছুতেই খাব না। (ইমাম মালিক)
ইসলাম ঘুষ-রিশওয়াত হারাম করেছেন, এটা কোন আশ্চর্যের ব্যাপার নয়। এতে যে যে লোক শরীক হয়, তাদের ব্যাপারেও কঠোরতা অবলম্বন করেছে, তাও বিচিত্র নয়। কেননা যে সমাজে এর ব্যাপকতা হয়, সে সমাজ জুলুমে জর্জরিত হতে বাধ্য এবং তার ধ্বংস অনিবার্য। যে লোক অন্যায়ভাবে প্রশাসন চালানো বা বিচারের রায় দিল কিংবা সত্য ও ন্যয়ভিত্তিক বিচার করতে প্রশাসন অস্বীকার করল। যে পিছনে তাকে অগ্রে এনে দিল এবং যে অগ্রবর্তী তাকে পশ্চাদবর্তী করে দিল, সে সমাজে কর্তব্যপরায়ণতার ভাবধারার পরিবর্তে স্বার্থপরতার ভাবধারা প্রবল হয়ে দেখা দেয়।
শাসক – প্রশাসকদের জন্যে উপটৌকন
ঘুষ- তা যে কোন রূপ যে কোন নামেই হোক, ইসলাম তা হারাম ঘোষণা করেছে। তাকে যদি হাদিয়া-তোহফা বা উপহার-উপটৌকন বলা হয় তবু তা হারামের গণ্ডি থেকে বের হয়ে হালালের আওতার মধ্যে পড়বে না।
হাদীসে উদ্ধৃত হয়েছে, রাসূলে করীম (সা) বলেছেনঃ ( আরবি*******************)
যে লোককে আমরা কোন কাজে নিযুক্ত করেছি ও তার বেতন নির্দিষ্ট করে ধার্য করে দিয়েছি, সে যদি তার পরও কিছু গ্রহন করে, তবে তা হবে খিয়ানত। (আবূ দাঊদ)
খলীফা উমর ইবনে আবদুল আজীজের সম্মুখে কিছু হাদিয়া পেশ করা হয়। তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। তখন তাঁকে বলা হয়ঃ স্বয়ং রাসূলে করীম (সা) হাদিয়া-তোহফা গ্রহণ করতেন আর আপনি করছেন না? জবাবে তিনি বললেনঃ হ্যাঁ, তা তো তাঁর জন্যে ‘হাদিয়াই ছিল কিন্তু তা আমাদের জন্যে ঘুষ ছাড়া আর কিছু নয়।
রাসূলে করীম (সা) সাদকা যাকাত সংগ্রহের দায়িত্ব দিয়ে আজদ গোত্রের কাছে লোক পাঠিয়েছিলেন। সে যখন তাঁর কাছে ফিরে এল তখন কিছু ধনমাল নিজের হাতে রেখে দিয়ে বললঃ এ মাল আপনার আর এসব আমাকে উপটৌকন হিসেবে দেয়া হয়েছে। এ কথা শুনে নবী করীম (সা) খুবই রাগান্বিত হলেন এবং বললেনঃ ( আরবি*******************)
তোমার এ কথাই যদি সত্য হয়, তাহলে তুমি তোমার মা-বাবার ঘরে বসে থাকতে, তখন দেখা যেত, কে তোমাকে হাদিয়া দিচ্ছে ? পরে বলেছেনঃ ( আরবি*******************)
ব্যাপর কি, আমি তোমাদের মধ্য থেকে একজনকে সরকারী কর্মচারী নিযুক্ত করি। পরে সে বলেঃ প্রাপ্ত ধনমালের এ অংশ আপনার আর এ অংশ আমার জন্যে হাদিয়া বাবদ দেয়া? সে কেন তার মায়ের ঘরে বসে থাকেনি, তারপর যদি হাদিয়া দেয়া হতো তাহলে না হয় তার এ কথার যথার্থতা বোঝা যেত। যাঁর হাতে আমার জীবন তার শপথ, তোমাদের কেউ যদি নাহকভাবে কোন ধনমাল গ্রহণ করে তাহলে কিয়ামতের দিন তাকে তা আল্লাহর কাছে বহন করে নিয়ে উপস্থিত হতে হবে। তাই তোমরা কিয়ামতের দিন যেন নিজেদের কাঁধে করে উষ্ট্র, গরু-গাভী বা ছাগল নিয়ে আসতে বাধ্য না হও- এরূপ অবস্থায় যে, সে জন্তুটি চিৎকার করছে। পরে তিনি তাঁর দুই হস্ত ঊর্ধ্বে উত্তোলিত করলেন এতটা যে, তার দুহাতের বগলের সাদা অংশ দৃশ্যমান হয়ে উঠল। অতঃপর বললেনঃ হে আল্লাহ্! আমি কি কথা পৌঁছে দিয়েছি?
ইমাম গাযযালী বলেছেনঃ ঘুষের ব্যাপারে এসব কঠোরতা ও তীব্রতা প্রচণ্ডতা দেখে বলতে হয় যে, বিচারক প্রশাসক কিংবা তাদের মতো দায়ীত্বশীল ব্যক্তিদের উচিত তাদের মা-বাবার ঘরে বসে থাকা। তাদের পদচ্যুত করে দেয়ার পর তাদের মায়ের ঘরে থাকা অবস্থায় তাদের যদি ‘হাদিয়া-তোহফ’ দেয়া হয়, তাহলে তা গ্রহণ করা তাদের জন্যে জায়েয হতে পারে, পদে অভিষিক্ত থাকা অবস্থায়ও। আর যে সম্পর্কে জানতে পারবে যে, তা তার পদে অভিষিক্ত থাকার কারণেই দেয়া হয়েছে, তা গ্রহণ করা সম্পূর্ণ হারাম। আর বন্ধু-বান্ধবদের দেয়া হাদিয়া-তোহফা যদি পদচুত হওয়ার পরও দিত বলে জানা না যায়, তাহলে তাতে সন্দেহ রয়েছে। কাজেই তা পরিহার করা কর্তব্য। ( আরবি*******************)
জুলুম বন্ধের জন্যে ঘুষ দেয়া
অবস্থা যদি এমন হয়ে দাঁড়ায় যে, নিজের ন্যায্য হকও ঘুষ না দিলে পাওয়ার কোন উপায় নেই কিংবা এমন জুলুমের মধ্যে পড়ে গেছে যে, ঘুষ না দিলে তা থেকে নিষ্কৃতি কোনক্রমেই সম্ভবপর নয়, তাহলে তার ধৈর্য ধারণ ও সবর ইখতিয়ার করা উচিত, যতক্ষণ না আল্লাহই তার জন্যে হক পাওয়া ও জুলুম মুক্তির কোন উত্তম পথ ও পন্থা করে দেন।
এ কারণে ঘুষের পথে অগ্রসর হলে ঘুষ গ্রহণকারীই গুনাগার হবে। এরূপ অবস্থায় ঘুষদাতা গুনাহগার হবে না, যদি অন্যান্য হালাল সব পথই যাচাই করে দেখে ফল না পেয়ে শেষ উপায় হিসেবে তা অবলম্বন করে ও সেই সাথে সে যদি শুধু নিজের ওপর থেকে জুলুম বিদুরণ ও ন্যায্য হক পাওয়া এবং অন্যান্যদের অধিকারে হস্তক্ষেপ না করে থাকতে পারে।
কোন কোন আলিম এই মতের সমর্থন দলিল স্বরূপ উল্লেখ করেছেন সেসব হাদীস, যাতে উল্লেখিত হয়েছে যে, একদল লোক রাসূলে করীম (সা)-কে জড়িয়ে ধরত সাদকা পাওয়ার জন্যে। তখন ওরা কিছু পাওয়ার ন্যায় অধিকারী না হওয়া সত্ত্বেও তিনি এদের কিছু দিয়ে দিতেন। হযরত উমর (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম (সা) বলেছেনঃ ( আরবি*******************)
তোমাদের কেউ কেউ আমার কাছ থেকে সাদকার মাল নিয়ে বগলে চেপে বের হয়ে যায় অথচ তা তার জন্যে আগুন। হযরত উমর (রা) বললেনঃ আপনি নিজেই যখন জানেন যে, তা তার জন্যে আগুন, তখন আপনি তাকে দেন কেন?
জবাবে বললেনঃ আমি কি করব? ওরা এমনভাবে চাইতে থাকে ও ধরে বসে যে, ওদের ছাড়ানই যায় না। আর আল্লাহ্ মহান মহিম চান না যে, আমি কার্পণ্য করি।
বারবার ও চেপে ধরে চাওয়ার দরুন রাসূলে করীম (সা) যখন প্রার্থীকে কিছু না কিছু ধন-মাল দিতেন, একথা জেনেও দিতেন যে, তা তার জন্যে আগুন, তাহলে জুলুম বন্ধ করা ও নিজের ন্যায্য হক ও পাওনা আদায়ের প্রয়োজনে ঘুষ দেয়া জায়েয হবে না কেন?
নিজেদের ধন-মাল অপব্যয় করা
প্রত্যেকের পক্ষে অন্য লোকের ধন-মালের যেমন একটা মর্যাদা আছে, তাতে গোপনে কিংবা প্রকাশ্যে কোনরূপ সীমালংঘনমূলক হস্তক্ষেপ যেমন হারাম, অনুরূপভাবে প্রত্যেকের কাছে তার নিজের ধন-মালেরও একটা মর্যাদা রয়েছে। সেজন্যে সে ধন-মাল অপচয় অপব্যয় করা, নষ্ট করা, ধ্বংস করা, কিংবা ডান হাতে বাম হাতে ছিটানও সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।
তা এজন্যে যে, ব্যক্তিগণের ধন-মালে জাতি ও সমাজ-সমষ্টির হক রয়েছে। সব মালিকের উর্ধ্বে তার মালিকানা অধিকার অবশ্যিই স্বীকৃতব্য। এ করণেই যে নির্বোধ ধন-মালিক স্বীয় ধন-মাল বিনষ্ট করে, সমাজের অধিকার ও কর্তৃত্ব রয়েছে তার ওপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম করার। কেননা সে ধন-মালে সমাজ সমষ্টিরও অংশ কয়েছে। এ পর্যায়ে কুরআন মজীদ বলেছেঃ ( আরবি*******************)
তোমরা নির্বোধ লোকদেরকে দিও না তোমাদের ধন-মাল, যাকে আল্লাহ্ তা’আলা তোমাদের জন্যে উপজীব্য বা প্রতিষ্ঠার বাহন বানিয়েছেন, আর তাদের রিযক দাও তা থেকে এবং তাদের জন্যে ভাল ও উত্তম প্রচলিত কথা বল।
এ আয়াতে আল্লাহ্ তা’আলা মূলত সম্বোধন করেছেন সমাজ-সমষ্টিকেঃ তোমরা দিও না তোমাদের ধন-মাল বলে। যদিও বাহ্যত এ ধন-মাল ব্যক্তিদের নিজ মালিকানার। কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তির ধন-মাল আসলে গোটা সমাজ সমষ্টিরই জাতীয় সম্পদ।
বস্তুত ইসলাম সুবিচার, ইনসাফ ও ভারসাম্যতার দ্বীন। আর মুসলিম উম্মত হচ্ছে মধ্যম অর্থাৎ মধ্যম নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত উম্মত। মুসলমানের আদর্শ হচ্ছে সর্বক্ষেত্রে সুবিচার ও ন্যায়পরতা প্রতিষ্ঠা। এ কারণেই আল্লাহ্ তা’আলা মুমিনদের স্পষ্ট ও কঠোর ভাষায় নিষেধ করেছেন ধন-মালের অপব্যয় ও অপচয় করতে যেমন নিষেধ করেছেন কার্পণ্য ও বখিলি করতে। বলেছেনঃ ( আরবি*******************)
হে আদম সন্তান! তোমরা প্রত্যেকবার মসজিদে উপস্থিতিকালে তোমাদের সৌন্দর্য-অলংকার গ্রহণ কর। আর তোমরা খাও, পান কর, কিন্তু অপব্যয়-অপচয় করবে না। কেননা আল্লাহ্ অপব্যয় অপচয়কারীকে পছন্দ করেন না।
আল্লাহর হারাম করে দেয়া কাজে ধন-সম্পদ ব্যয় করা হলেও অপচয় অপব্যয়ই হবে, যেমন মদ্যপান, বিবেক-বুদ্ধি আচ্ছন্নকারী দ্রব্যাদি, স্বর্ণ-রৌপ্যের পাত্রাদি ক্রয় ইত্যাদি এ ক্ষেত্রে ব্যয় করা ধন-মালের পরিমান কম হোক, বেশি হোক, সবই নিষিদ্ধ।
ধন-মাল নিজের জন্যে বা অন্য লোকদের জন্যে অপব্যয় কারারও কোন অনুমতি নেই ইসলামে। নবী করীম (সা) ধন-মাল বিনষ্ট করতে স্পষ্ট ভাষয় নিষেধ করেছেন। (বুখারী)
অপ্রয়োজনীয় কাজে খুব বেশি অর্থব্যয় ও অপচয় অপব্যয় ছাড়া আর কিছু নয়। এরূপ অপব্যয়-অপচয় মানুষকে সর্বস্বান্ত করে দেয়। শেষ পর্যন্ত নিজের কাছে এমন পরিমাণ সম্পদও থাকে না, যদ্বারা নিজের মৌলিক প্রয়োজনটুকুও পূরণ করা যেতে পারে।
কুরআন মজীদের আয়াতঃ ( আরবি*******************)
লোকেরা তেমার কাছে- হে নবী- জিজ্ঞেস করে, তারা কি ব্যয় করবে? বল- আল-আফওয়া। (সূরা বাকারাঃ ২১৯)
এ আয়াতের তাফসীরে ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী লিখেছেনঃ
আল্লাহ্ তা’আলা লোকদের অর্থ সম্পদ ব্যয় করার নিয়ম-পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন। উক্ত আয়াতে নবী করীম (সা)-কে সম্বোধন করে বলেছেনঃ আত্মীয়দের তাদের হক দাও, মিসকীন ও মুসাফিরকেও এবং বেহুদা অর্থ ব্যয় করবে না। বেহুদা ব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই পর্যায়ে গণ্য। (আল-ইমরান-২৬) এবং বলেছেনঃ তুমি তোমরা হস্ত নিজের গলার সঙ্গে বেঁধে রেখো না, আর তাকে একেবারে খুলেও দিওনা। (আল-ইমরান-২৯) বলেছেনঃ যারা ব্যয় করে, কিন্তু না অপব্যয় করে, না সংকীর্ণতার প্রশ্রয় দেয় (আল-ফুরকান-৬৭) আর নবী করীম (সা) বলেছেনঃ তোমাদের কারো কাছে ধন-মাল থাকলে তার ব্যয় শুরু করবে নিজের থেকে। পরে যারা তার ভরণ-পোষণের দায়িত্বাধীন লোক তাদের জন্যে আর তাদের পরে অন্যান্যদের জন্যে ব্যয় করবে। (মুসলিম) বলেছেনঃ সর্বোত্তম সাদকা হচ্ছে তা যা করা হলে ব্যক্তিকে সচ্ছল থাকতে দেয়। (তাবারানী) হযরত জাবীর ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেনঃ আমরা রাসূলে করীম (সা)-এর দরবরে উপস্থিত ছিলাম। এক ব্যক্তি ডিমের সমান পরিমাণ স্বর্ণ নিয়ে তাথায় উপস্থিত হলো এবং বললঃ এটা দান হিসেবে কবুল করুন। আল্লাহর শপথ। আমার কাছে এ ছাড়া আর কিছু নেই। নবী করীম (সা) তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। কিন্তু সে ব্যক্তি আবার সম্মুখে উপস্থিত হলো। তখন তিনি বললেনঃ দাও। খুব অসন্তুষ্টি ও ক্রোধ সহকারে তা গ্রহণ করে সেটি তার দিকে এমনভাবে নিক্ষেপ করলেন যে, কারো দেহে লেগে গেলে সে আঘাত পেত। পরে বললেনঃ তোমাদের এক-একজন তার সমস্ত ধন-সম্পদ নিয়ে আসে, পরে সে লোকদের সামনে হস্ত প্রসারিত করে ভিক্ষার জন্যে বসে। দান সাদকা তো তা-ই যা সচ্ছল অবস্থার ব্যক্তির সচ্ছলতাকে অক্ষুণ্ণ রেখে করা হবে। এটা নিয়ে নাও, আমার কোন প্রয়োজন নেই তাতে। (আবূ দাঊদ, হাকেম) নবী করীম (সা) তাঁর ঘরের লোকদের জন্যে এক বছরের খাবার জমা করে রাখতেন। (বুখারী)। বুদ্ধিমানরা বলেন, বেশি বাড়াবাড়ি ও প্রয়োজনের চাইতেও কম- এ দুই প্রান্তিকের মধ্যবর্তী নীতিই উত্তম। প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যয় করা বেহুদা খরচ। আর কম ব্যয় করা কার্পণ্য, বখিলি। ভারসাম্যপূর্ণ নীতিই সর্বোত্তম আর ‘বল আল-আফওয়া’ বলে তা-ই বলেছেন আল্লাহ্ তা’আলা। এ সূক্ষ্ম ও নিগূঢ় তত্ত্ব অনুধাবন ও সংরক্ষণের ওপরই মুহাম্মাদী শরীয়ত নির্ভরশীল। কেননা ইয়াহূদী শরীয়ত কৃচ্ছতা কঠোরতার ওপর প্রতিষ্ঠিত। আর খ্রিস্টানদের ধর্ম-বিধান পরম ঔদার্য ও ঢিলা নীতির অনুসারী। এ সব ব্যাপারে মুহাম্মাদী শরীয়তই মধ্যম নীতির ধারক ও প্রবর্তক। এ কারণে তা অপর শরীয়তগুলোর তুলনায় অতীব পূর্ণাঙ্গ ও পূর্ণ পরিণত বিধান (তাফসীর, ফখরুদ্দীন রাযী, ৬ষ্ঠ খণ্ড)
অমুসলিমের সাথে সম্পর্ক
দ্বীন-ইমলামের বিরুদ্ধবাদীদের সাথে আচার-আচরণ অবলম্বনের ব্যাপারে ইসলামের নীতি ও আদর্শকে সংক্ষেপে বলতে হলে কুরআন মজীদের দুটি আয়াতের উল্লেখই যথেষ্ট। এ আয়াত দুটি এ পর্যাযে ব্যাপক সংবিধান হওয়ার উপযুক্ত। তা হচ্ছে, আল্লাহ্ তা’আলা ইরশাদ করেছেনঃ ( আরবি*******************)
আল্লাহ্ তা’আলা তোমাদের সেই লোকদের সাথে ভাল ও সুবিচারমূলক আচরণ গ্রহণ করতে নিষেধ করছেন না, যারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদের ঘর থেকে তোমাদের বহিষ্কৃত করেনি। আল্লাহ্ তো সুবিচারকারীদের পছন্দ করেন। তিনি তোমাদের বিরত রাখছেন শুধু এ থেকে যে, তোমরা বন্ধুতা করবে না তাদের সাথে, যারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেছে ও তোমাদের ঘর থেকে তোমাদের বহিষ্কৃত করেছে এবং তোমাদের বহিষ্কৃতকরণে পরস্পরের সাথে সহযোগিতা করেছে। এ লোকদের সাথে যারা বন্ধুতা করবে, তারাই জালিম।
যাদের সাথে মুসলমানদের যুদ্ধ বা কোনরূপ শত্রুতা নেই, যারা দ্বীনের ব্যাপার নিয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি ও তাদের ঘর থেকে বহিষ্কৃতও করেনি, প্রথমোক্ত আয়াতে তাদের প্রতি শুধু সুবিচার ও ন্যায়পরতা গ্রহণের উৎসাহ দেয়া হয়নি; বরং তাদের প্রতি ভাল ও শুভ আচরণ করণ ও তাদের কল্যাণ সাধনের জন্যে উৎসাহিত করা হয়েছে। আয়াতে ব্যবহৃত ( আরবি*******************) শব্দটি কল্যাণ ও মঙ্গলের ব্যাপক অর্থবোধক, সুবিচার ও ন্যায়পরতারও ঊর্ধ্বে তা, মানবীয় অধিকারের সর্বোচ্চ মান বুজে থাকেন মুমলমানরা এই শব্দ থেকে। যেমন ( আরবি*******************) বলতে পিতামাতার অধিকার আদায়ে পূর্ণ মাত্রায় কল্যাণ সাধন বুঝে থাকে। এই পর্যায়ে কুরআনের কথা হলোঃ ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সুবিচার ও ন্যায়পরতাকারীদের ভালবাসেল।’ আর ঈমানদার লোক মাত্রই সব সময় সে কাজ করতেই অধিক ভালবাসে, তৎপর হয়, যা আল্লাহ্ পছন্দ করেন- ভালবাসেন। এতো সর্বজনবিদিত।
‘আল্লাহ্ তোমাদের নিষেধ করছেন না’ কথায় ভাল আচরণ গ্রহণ ইপ্সিত হওয়াটার বিপরীত কিছু বোঝায় না। কথা বলার এই ধরনটি গ্রহণ করা হয়েছে এজন্যে যে, মুসলমানরা হয়ত মনে করতে পারেন যে, দ্বীনের বিরুদ্ধপন্থীরা বুঝি ভাল আচরন ও ন্যায়পরতা পাওয়ার অধিকারী নয়। এই ভুল ধারনা দূর করার উদ্দেশ্রে স্পষ্ট করে বলা হলো যে, আল্লাহ্ বিরোধীদের সাধে ভাল আচরণ গ্রহণ, বন্ধুতা ও সুবিচার করা থেকে বিরত রাখেন না- তা করতে নিষেধ করছেন না। তিনি শুধু সেসব লোকদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখতে নিষেধ করেন যারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত এবং তাদের বিরুদ্ধে আগ্রাসন গ্রহণ করছে।
এখানকার এ কথার ধরন ঠিক অপর একটি আয়াতের মতোই। আয়াতটি হচ্ছেঃ ( আরবি*******************)
যে লোক হজ্জ্ব করল কিংবা উমরা করল, তাদের ওপর কোন দোষ নেই যদি তারা সাফা-মারওয়ার তওয়াফ করে।
কথা বলার এ ভঙ্গির কারণ হচ্ছে কতিপয় লোক জাহিলিয়াত আমলের নিদর্শনাবলীর কারণে ইসলামের আমলেও পর্বতদ্বয়ের তওয়াফ করতে দ্বিধাবোধ করেছিলেন, সেই দ্বিধা-সংকোচ দূর করাই প্রথম লক্ষ্য। ‘দোষ নেই’ বলা হলো দ্বিধা দূর করার উদ্দেশ্যে, যদিও এ দুটো পর্বতের তাওয়াফ করা ওয়াজিব এবং হজ্জের জরুরী অনুষ্ঠানের মধ্যে গণ্য।
আহলি কিতাবের প্রতি বিশেষ সুবিধা দান
ইসলাম যখন দ্বীন-ইসলামের বিরোধীদের সাথেই সর্বোচ্চ মানের ভাল ব্যবহার ও ন্যায়পরতা গ্রহণ থেকে নিষেধ করে না, মূর্তি পূজারী মুশরিক হলেও নয়- যেমন প্রথমে উদ্ধৃত আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে, যা আরবের মুশরিকদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছিল। তখন আহলি কিতাব- ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানদের প্রতি যে ইসলাম বিশেষ সুবিধাদি দান করবে- তারা ইসলামী দেশের অধিবাসী হোক কি তার বাইরে- তা তো অতি স্বাভাবিক।
কুরআন মজীদে এই ইয়াহূদী খ্রিস্টানদের সম্বোধন করা হয়েছে আহলি ‘কিতাব’- সেই লোক যাদের কিতাব দেয়া হয়েছে- বলে। এ থেকে বোঝাতে চেয়েছে যে, আসলে এরা আল্লাহর নাযিল করা দ্বীনের ধারক লোক। অতএব মুসলমান ও তাদের মাঝে নিকটাত্মীয়তা সম্পর্ক রয়েছে। আল্লাহ্ তা’আলা তাঁর নবী-রাসূলগণকে যে মৌল দ্বীন ও বিধান সহ পাঠিয়েছেন, আসলে তা এক ও অভিন্ন। একটি আয়াত উল্লেখ্যঃ ( আরবি*******************)
তিনি তোমাদের জন্যে সেই দ্বীনই সুনির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, যার নির্দেশ তিনি নূহকে দিয়েছিলেন, আর যা আমরা তোমার প্রতি ওহী করে পাঠিয়েছি, আর তার পথ-নির্দেশ করেছিলাম ইবরাহীম, মূসা ও ঈসকে এই বলে যে, তোমরা সকলে এই দ্বীনকে কায়েম কর এবং এ ব্যাপারে ভিন্ন ভিন্ন ও ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যেও না। (সূরা শূরাঃ ১৩)
মুসলমানদের তো নির্দেশ দেয়া হয়েছে আল্লাহর নাযিল করা সমস্ত কিতাবের প্রতি ঈমান গ্রহণের জন্যে। তাই সব নবী-রাসূলের প্রতি ঈমান গ্রহণ মুসলমানের কর্তব্য। এছাড়া তাদের ঈমান সত্য ও যথার্থই হতে পারে না। বলা হয়েছেঃ ( আরবি*******************)
তোমরা বলঃ আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর প্রতি ও যা নাযিল হয়েছে আমাদের প্রতি, আর যা নাযিল হয়েছে ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও বংশধরদের প্রতি, আর যা দেয়া হয়েছে মূসা, ঈসা ও আল্লাহর প্রেরিত নবীগণের প্রতি- আমরা তাদের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য করি না, আমরা তো সেই এক আল্লাহরই অনুগত। (সূরা বাকারাঃ ১৩৬)
আহলি কিতাবের লোকেরা যখন কুরআন পাঠ করে তখন তারা দেখতে পায়, কুরআনে তাদের ধর্ম গ্রন্থের ও নবী-রাসূলগণের উচ্চ প্রশংসা করা হয়েছে। অতএব মুসলমানরা যখন আহলি কিতাবের লোকদের সাথে তর্ক-বিতর্কে অবতীর্ণ হবে, তখন অবশ্যই এমন সব কথাবার্তা বলা থেকে বিরত থাকবে যা পারস্পরিক ঘৃণা ও বিদ্বেষ বৃদ্ধি করে। বলা হয়েছেঃ ( আরবি*******************)
আহলি কিতাবের সাথে বিতর্ক করো না- তবে উত্তম পন্থায়, তাদের ছাড়া, যারা ওদের মধ্যে জালিম। আর বল, আমরা ঈমান এনেছি সেই জিনেসের প্রতি, যা আমাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে, সে জিনিসেরও যা তোমাদের প্রতি নাযিল হয়েছে। আমাদের ইলাহ ও তোমাদের ইলাহ এক ও অভিন্ন। আর আমরা তাঁরই অনুগত- আত্মসমর্পিত। (সূরা আনকাবুতঃ ৪৬)
আহলি কিতাবের সাথে পানাহার করা ও তাদের যবেহ করা জন্তু খাওয়া এবং তাদের মেয়ে বিয়ে করা- যদিও বিয়েটা পরম প্রীতি ও ভালবাসার লীলাকেন্দ্র- জায়েয করে দিয়ে ইসলাম যে উদার নীতি অবলম্বন করেছে তার বিস্তারিত আলোচনা আমরা করেছি। এ পর্যায়ে নিম্নোক্ত আয়াতটি উল্লেখ্যঃ ( আরবি*******************)
আহলি কিতাবের খাবার তোমাদের জন্যে হালাল, তোমাদের খাবারও হালাল তাদের জন্যে। আর সুরক্ষিতা পবিত্রা নারী মুসলমানদের ও তোমাদের পূর্বে কিতাব পাওয়া লোকদের- তাও হালাল। (সূরা মায়িদাঃ ৫)
আহলি কিতাবের ব্যাপারে এ হচ্ছে ইসলামের সাধারণ নীতি। তবে খ্রিস্টানদের প্রতি একটা বিশেষ ধরনের নীতি অবলম্বিত হয়েছে। কুরআন তো তাদের সম্পর্কে বলেছে, তারা মুসলমানদের হৃদয়ের নিবিড় নৈকট্যে অবস্থিত। বলেছেঃ ( আরবি*******************)
তোমরা ঈমানদার লোকদের বন্ধুত্বে নিকটবর্তী পাবে সেই লোকদের, যারা বলেছেঃ আমরা নাসারা-খ্রিস্টান। তা এজন্যে যে, তাদের মধ্যে বহু পণ্ডিত বিদ্বান রয়েছে, আর তারা অহংকার করে না। (সূরা মায়িদাঃ ৮২)
যিম্মি
উপরে যেসব উপদেশ উদ্ধৃত হয়েছে, তা সকল আহলি কিতাবকেই শামিল করে নেয়। তারা যেখানেই বসবাস করুক, কারো ব্যাপারে কোন ব্যতিক্রম নেই। তবে ইসলামী রাষ্ট্রের ছায়াতলে যে সব অমুসলিম বাস করে, তাদের জন্যে ইসলাম বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। মুসলিম পরিভাষায় তাদের বলা হয় ‘যিম্মী’। ‘যিম্মী’ শব্দের অর্থ ‘চুক্তি’- ওয়াদা। এ শব্দটি জানিয়ে দেয় যে, এদের জন্যে আল্লাহর এবং তার রাসূলের একটা ওয়াদা বয়েছে। মুসলিম জামায়াত সে ওয়াদা পালনে বাধ্য। আর তা হচ্ছে এই যে, তারা ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে সম্পূর্ণ নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত- জীবন যাপন করতে পারবে।
আধুনিক ব্যাখ্যায় এরা ইসলামী রাষ্ট্রের অধিবাসী- নাগরিক। প্রথম দিন থেকেই মুসলিম সমাজ এ সময় পর্যন্ত এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ একমত যে, ইসলামী রাষ্ট্রে মুসলিমদের জন্যে যে অধিকার, অমুসলিমদের জন্যেও সেই অধিকার। তাদের যা দেয়-দায়িত্ব, এদেরও দায়-দায়িত্ব তা-ই। তবে শুধু আকিদা, বিশ্বাস ও দ্বীন-সংক্রান্ত ব্যাপারাদিতে তাদের সাথে কোন মিল বা সামঞ্জস্য নেই। কেননা ইসলাম তাদেরকে তাদের দ্বীন ধর্মের ওপর বহাল থাকার পূর্ণ আযাদী দিয়েছেন।
যিম্মীদের সম্পর্কে নবী করীম (সা) খুব কড়া ভাষায় মুসলমানদের নসীহত করেছেন এবং সেই নসীহতের বিরোধিতা বা লংঘন হলে আল্লাহর অসন্তোষ অবধারিত বলে জানিয়েছেন। হাদীসে নবী করীমের কথা উদ্ধৃত হয়েছেঃ ( আরবি*******************)
যে লোক কোন যিম্মীকে কষ্ট বা জ্বালা-যন্ত্রণা দিল, সে যেন আমাকে কষ্ট ও জ্বালা-যন্ত্রণা দিল। আর যে লোক আমাকে জ্বালা-যন্ত্রণা ও কষ্ট দিল, সে মহান আল্লাহকে কষ্ট দিল। (তাবারানী ফিল আওসত)
( আরবি*******************) যে লোক কোন যিম্মীকে কষ্ট দিল, আমি তার বিরুদ্ধে মামলা দায়েরকারী। আর আমি যার বিরুদ্ধে মামলা দায়েরকারী, তার বিরুদ্ধে কিয়ামতের দিন আমি মামলা লড়ব। (আল-খাতিব)
( আরবি*******************) যে লোক কোন চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তির ওপর জুলুম করবে কিংবা তার হক নষ্ট করবে অথবা শক্তি-সামর্থ্যের অধিক বোঝা তার ওপর চাপাবে কিংবা তার ইচ্ছা ও অনুমতি ছাড়া তার কোন জিনিস নিয়ে নেবে, কিয়ামতের দিন আমি তার বিরুদ্ধে মামলা লড়ব। (আবূ-দাঊদ)
রাসূলে করীম (সা)-এর খলীফাগণ এসব অমুসলিম নাগরিকদের অধিকার আদায় ও মর্যাদা রক্ষায় সব সময় সচেতন-সতর্ক থাকতেন। ইসলামের ফিকাহবিদগণ মতপার্থক্য থাকা সত্ত্বেও এ সব অধিকার ও মর্যাদার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন।
মালিকী মাযহাবের ফিকাহবিদ শিহাবুদ্দীন আল-কিরাফী বলেছেনঃ
যিম্মীদের সাথে কৃত চুক্তি আমাদের উপর তাদের কতিপয় আধিকার ওয়াজিব করে দিয়েছে। কেননা তারা আমাদের প্রতিবেশী হয়ে আমাদের সংরক্ষণ ও নিরাপত্তার অধীন এসে গেছে। আল্লাহ্, রাসূল ও দ্বীন-ইসলাম তাদের নিরাপত্তা দিয়েছে। কাজেই যে লোক তাদের ওপর কোন রকমের বাড়াবাড়ি করবে সামান্য মাত্রায় হলেও তা আল্লাহ্ তাঁর রাসূল এবং দ্বীন-ইসলামের দেয়া নিরাপত্তা বিনষ্ট করার অপরাধে অপরাধী হবে। তাদের খারাপ কথা বলা, তাদের মধ্যে থেকে কারো গীবত করা বা তাদের কোনরূপ কষ্ট জ্বালা দেয়া অথবা এ ধরনের কাজে সহযোগিতা করা ইত্যাদি সবই এ নিরাপত্তা বিনষ্টের দিক।
যাহেরী মাযহাবের ফিকাহবিদ ইবনে হাজম বলেছেনঃ
যেসব লোক যিম্মী, তাদের ওপর যদি কেউ আক্রমণ করতে আসে, তাহলে তাদের পক্ষ হয়ে সশস্ত্র যুদ্ধ করার জন্যে অগ্রসর হওয়া ও তাদের জন্যে মৃত্যুবরণ করা আমাদের কর্তব্য। তাহলেই আমরা আল্লাহ্ ও রাসূলের নিরাপত্তা দেয়া লোকদের সংরক্ষণ করতে পারব। কেননা এ রূপ অবস্থায় তাদের অসহায় ও সহজ শিকার হতে দেয়া নিরাপত্তা দেয়ার দায়িত্ব পালনের পক্ষে বড্ড ক্ষতিকারক হবে।
অমুসলিমদের সাথে সম্পর্কের রূপ
প্রশ্ন উঠতে পারে, অমুসলিমদের সাথে ভাল ব্যবহার ও সুসম্পর্ক স্থাপন কি করে সম্ভব, যখন কুরআন নিজেই কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব সম্পর্ক স্থাপন করতে ও তাদের নিজেদের মিত্র ও বন্ধু বানাতে নিষেধ করছে?
যেমন কুরআনে বলা হয়েছেঃ ( আরবি*******************)
হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানদের বন্ধু-পৃষ্ঠপোষক রূপে গ্রহণ করো না। ওরাই পরস্পরের বন্ধু! অতএব তোমাদের যে লোকই ওদের বন্ধু-পৃষ্ঠপোষকরূপে গ্রহণ করবে, সে তাদের মধ্যে গণ্য হবে। নিশ্চেয়ই আল্লাহ্ জালিমদের হেদায়েত করেন না। তুমি লক্ষ্য করছ, যাদের অন্তরে রোগ রয়েছে, তারা তাদেরা মধ্যেই দৌড়াদৌড়ি করে।
এ প্রশ্নের জবাব হচ্ছে, এসব আয়াত সাধারণভাবে প্রযোজ্য নয়। আর সব ইয়াহূদী-খ্রিস্টান-কাফির একই রকমের নয়। যদি তা-ই মনে করা হয়, তাহলে এ পর্যায়ের অন্যান্য আয়াত ও দলিল- যাতে যে কোন ধর্মাবলম্বী লোকদের সাথে কল্যাণকামী ও সদাচারী লোকদের সাথে ভাল আচরণ ও সুসম্পর্ক রক্ষার বৈধতা ঘোষিত হয়েছে- এর সাথে বৈপরীত্য ঘটবে। আহলি কিতাবের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন ও তাদের মেয়ে বিয়ে কারার অনুমতিও তো রয়েছে। অথচ বিয়ে সম্পর্কে আল্লাহ্ তা’আলা বলেছেনঃ ( আরবি*******************)
তিনি তোমাদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে গভীর প্রেম-প্রীতি, ভালবাসা ও দয়া সহানুভূতি সম্পন্ন সম্পর্ক স্থাপন করে দিয়েছেন।
আর খ্রিস্টানদের সম্পর্কে বলেছেনঃ ( আরবি*******************)
যারা বলেছেঃ আমরা নাসারা-খ্রিস্টান- ঈমানদার লোকদের সাথে বন্ধুতার ব্যাপারে তাদেরকে তুমি নিকটবর্তী পাবে।
বস্তুত যেসব আহলি কিতাবের সাথে বন্ধুতার সম্পর্ক স্থাপন নিষেধ রয়েছে তা প্রযোজ্য হচ্ছে দ্বীন-ইসলামে দুশমন ও মুসলমানের সাথে যুদ্ধ্যমান লোকদের ব্যাপারে। এ লোকদের সাহায্য করা, পৃষ্ঠপোষকতা করা- তাদের গোপন তথ্য জানান ও জাতীয় স্বার্থের বিরুদ্ধে তাদের মিত্র বানিয়ে তাদের অতি কাছে নিয়ে আসা কোন মুসলমানের পক্ষেই আদৌ জায়েয নয়। অন্যান্য আয়াতে এ কথা স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। একটি আয়াত উল্লেখ করা যায়ঃ ( আরবি*******************)
হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা তোমাদের ছাড়া অন্যদের অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে না। তারা তোমাদের ক্ষতি সাধন করতে কোন ত্রুটিই রাখবে না। যা তোমাদের জন্যে কষ্টদায়ক, ক্ষতিকর, বিপদজনক তা-ই তাদের মনপুতঃ তাদের শত্রুতা হিংসা-ক্রোধ তাদের মুক থেকেই প্রকাশিত হয়েছে। আর যা কিছু তারা নিজেদের মনে লুকিয়ে রেখেছে, তা তো তার চেয়েও অনেক বড়, ভীষণ। আমরা তোমাদের জন্যে আইন বিধান স্পষ্ট করে বলেছিলাম। এখন তোমরা যদি বুঝে শুনে কাজ কর। তোমরা সতর্ক থাকবে, তোমরা ওদের খুব ভালবাস; কিন্তু ওরা তোমাদের আদৌ পছন্দ করে না।
যাদের সাথে বন্ধুতার সম্পর্ক স্থাপন নিষিদ্ধ, উপরিউক্ত আয়াতে তাদের পরিচয় স্পষ্ট ভাষায় দিয়ে দেয়া হয়েছে। আসলে ওরা মুসলমানদের প্রতি চরম বক্রতা পোষণ করে অন্তরে লুকিয়ে রাখে। তা সত্ত্বেও তাদের মুখ থেকে তার নিদর্শনাদি প্রকাশ হয়ে পড়ে।
আল্লহ্ তা’আলা বলেছেনঃ ( আরবি*******************)
যারা আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি ঈমানদার, তাদের তুমি কখনও এমন লোকদের প্রতি বন্ধুতা পোষণ করতে দেখবে না, যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সাথে শত্রুতা পোষাণ করে। এরা তাদের বাপ-দাদা, সন্তান-সন্তাতি বা বংশের লোক হলেও। (সূরা মুজাদিলাঃ ২২)
বস্তুত আল্লাহ্ ও তার রাসূলের সাথে শত্রুতা পোষণ নিছক কুফরি নয়। তা হচ্ছে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে আগ্রাসন।
আল্লাহ্ বলেছেনঃ ( আরবি*******************)
হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রুকে বন্ধু- পৃষ্ঠপোষকরূপে গ্রহণ করো না- বানিও না। তোমরা তো ওদের প্রতি পরম বন্ধুতা-প্রীতি দেখাও। কিন্তু তোমাদের কাছে যে মহাসত্য এসেছে, ওরা তার প্রতি কুফরি করেছে। ওরা রাসূলকে এবং তোমাদের বহিষ্কৃত করে শুধু এই অপরাধে যে, তোমরা ঈমানদার তোমাদের রব্ব আল্লাহর প্রতি।
মক্কার যেসব মুশরিক আল্লাহ্ ও রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল এবং মুসলমানদেরকে তারা তাদের ঘর-বাড়ি থেকে বহিষ্কৃত করেছিল। শুধু মাত্র একটুকু অপরাধে যে, তাঁরা বলেছিলেন, আমাদের রব্ব হচ্ছেন আল্লাহ্। উপরিউক্ত আয়াত তাদের সম্পর্কেই নাযিল হয়েছিল। তাই এ ধরনের লোকদের সাথে বন্ধুতা-ভালবাসা স্থাপন করা মুসলমানদের জন্যে কখনোই জায়েয নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও ওদের অন্তরের পরিষ্কার পরিছন্ন হওয়ার ব্যাপারে কুরআন চূড়ান্তভাবে নৈরাশ্যের কথা বলেনি। বরং ওদের এ মন-মানসিকতারও যে পরিবর্তন পতে পারে এবং এখনকার মতো শত্রুতার মনোভাব একদির না-ও থাকতে পারে, এ আশাবাদই প্রকাশ করা হয়েছে। উপরোদ্ধৃত আয়াতের পরই বলা হয়েছেঃ ( আরবি*******************)
এটা খুব একটা অসম্ভব বা বিস্ময়কর নয় যে, আল্লাহ্ তোমাদের ও যাদের প্রতি তোমরা শত্রুতা পোষণ কর- যাদের শত্রুতার তোমরা আশংকা কর, তাদের মধ্যে বন্ধুতা-প্রীতির সৃষ্টি করে দেবেন। আল্লহ্ তো মহাশক্তিমান। আর আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়াবান। (সূরা মুমতাহিনাঃ ৭)
এটা কুরআনের সতর্ক বাণী। এ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, শত্রুতা পোষণ ও ঝগড়া-বিবাদের একটা সীমা নির্ধারণ একান্তই প্রয়োজনীয়। এর আলোকে বিচার করলে শত্রুতার মাত্রা তো অনেক হ্রাস পেয়ে যায়। হাদীসেও তাই বলা হয়েছেঃ ( আরবি*******************)
তোমার শত্রুর প্রতি বিদ্বেষ ভাবাটা খানিকটা কম করে রাখবে। কেননা সে তো একদিন তোমার একজন বন্ধুও হয়ে যেতে পারে।
শত্রু পক্ষ যখন খুব শক্তিশালী হয় যে, লোকেরা তাদের প্রতি আশাও পোষণ করে, তাদের ভয়ও করে, তাহলে এরূপ অবস্থায় তাদের সাথে বন্ধুতা-প্রীতির সম্পর্ক স্থাপন অধিকতর বেশি ও তীব্রভাবে হারাম হয়ে যায়। কেননা এরূপ অবস্থায় মুনাফিক ও অন্তরের রোগীরাই তাদের সাথে বন্ধুতা করার ব্যাপারে খুব অগ্রসর থাকবে। তাদের সাথে একটা গোপন সম্পর্ক রক্ষা করে চলবে, যেন কাল তা তাদের ফায়াদা দিতে পারে। যেমন আল্লাহ্ বলেছেনঃ ( আরবি*******************)
যাদের অন্তরে রোগ, ওদের দেখবে তারা সব সময় সেই লোকদের মধ্যে দৌড়াদৌড়ি করে- তৎপরতা দেখায়। বলে- আমরা ভয় পাই। আমরা বিপদের আবর্তে পরে না যাই। কিন্তু খুব সম্ভব আল্লাহ্ তোমাদের জয়দান করবেন কিংবা নিজের কাছ থেকে অন্য কিছু প্রকাশ করে দেবেন, তখন এরা নিজেদের অন্তরে যা কিছু লুকিয়ে রেখেছে তাতে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হবে। (সূরা মায়িদাঃ ৫২) ( আরবি*******************)
মুনাফিকদের সুসংবাদ দও যে, তাদের জন্যে পীড়াদায়ক আযাব নির্দিষ্ট রয়েছে। ওরা তারাই, যারা মুমিনদের বাদ দিয়ে কাফিরদের সাথে বন্ধুতা করে- তাদের পৃষ্ঠপোষক বানায়। ওরা কি তাদের কাছে ইজ্জত বা শক্তি-ক্ষমতা পেতে চায়? আসলে সমস্ত ইজ্জত-শক্তি ক্ষমতা-আধিপত্য সবই আল্লাহর। (সূরা আন-নিসাঃ ১৩৮-১৩৯)
অমুসলমানের কাছে সাহায্য চাওয়া
মুসলিম অমুসলিমের কাছে দ্বীনী ব্যাপারাদি ছাড়া চিকিৎসা, শিল্প, কৃষি প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক বিষয়াদিতে সাহায্য চাইতে পারে, তাতে কোন দোষ নেই। শাসন কর্তৃপক্ষ এবং সাধারণ মানুষ সকলের জন্যেই এ অনুমতি রয়েছে। তবে একথা অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ যে, এ সব ক্ষেত্রেই মুসলমানদের স্বনির্ভরতা ও স্বয়ং-সম্পূর্ণতা অর্জন করা একান্তই কর্তব্য।
নবী করীম (সা) নিজে অমুসলিমের কাছ থেকে বিভিন্ন কাজে ও ক্ষেত্রে মজুরীর বিনিময়ে সাহায্য নিয়েছেন, কাজ করিয়েছেন। হিজরত করার সময় পথ দেখানর উদ্দেশ্যে তিনি মক্কার মুশরিক আবদুল্লাহ ইবনে আরীকতের সাহায্য গ্রহণ করেছেন। আলিমগণ বলেনঃ কেউ কাফির হলে যে-কোন বিষয়েই তাকে বিশ্বাস করা যাবে না, এমন কথা জরুরী নয়। মদীনার পথে মক্কা ত্যাগ করার মতো কাজে পথ দেখিয়ে সাহায্য করার জন্যে একজন মুমরিকের সাহায্য গ্রহণ করায় এ পর্যায়ের সব দ্বিধা-দ্বন্দ্ব সহজেই দূর হয়ে যায়।
সবচেয়ে বড় কথা, মুসলমানের নেতার পক্ষে অমুসলিমের কাছে সাহায্য চাওয়া বিশেষ করে আহলিকিতাবের লোকদের কাছে- সম্পূর্ণ জায়েয বলে বিশষজ্ঞ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যুদ্ধে এদের শরীক করা ও বিজয় লাভ হলে মুসলমানদের ন্যায় তাদেরও গনিমতের মাল দিয়েছেন। হুনাইন যুদ্ধে ছওয়ান ইবনে উমাইয়া মুশরিক পওয়া সত্ত্বেও রাসূলে করীম (সা)-এর সঙ্গী হয়ে যুদ্ধ করেছেন।
তবে শর্ত এই যে, যে-অমুসলিমের সাহায্য গ্রহণ করা হবে, মুসলমানদের ব্যাপারে তার ভাল মত ও দৃষ্টিভঙ্গি থাকতে হবে। যদি তাদের বিশ্বাস করা না যায়, তাহলে অবশ্য সাহায্য গ্রহণ জায়েয হবে না। কেননা বিশ্বাস-অযোগ্য মুসলমানের সাহায্য গ্রহণই যখন নিষিদ্ধ, তখন বিশ্বাস-অযোগ্য কাফিরের সাহায্য গ্রহণের তো কোন প্রশ্নই উঠে না।
মুসলিম অমুসলিমকে হাদিয়া তোহফা দিতে পারে, তার দেয়া হাদিয়া তোহফা গ্রহণও করতে পারে। নবী করীম (সা) অমুসলিম রাজা-বাদশাদের দেয়া হাদিয়া-তোহফা কবুল করেছেন। এ পর্যায়ে বহু সংখ্যাক হাদীস বর্ণিত ও উদ্ধৃত হয়েছে। নবী-বেগম হযরত উম্মে সালমা (রা)-কে নবী করীম (সা) বলেছিলেনঃ ( আরবি*******************)
আমি নাজ্জাশী বাদশাকে রেশমী চাদর ইত্যাদি তোহফা পাঠিয়েছিলাম।
বস্তুত ইসলাম মানুষকে মানুষ হিসেবেই মর্যাদা দেয়, সম্মান করে। তাহেলে আহলি কিতাব, যিম্মী ও চুক্তিবদ্ধ কোন মানুষের সাথে অনুরূপ মর্যাদাপূর্ণ ব্যবহার ও আচরণ অবলম্বিত হবে না কেন?
নবী করীম (সা)-এর কাছ দিয়ে একটি জানাযা নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। তা দিখে তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন। তখন তাঁকে বলা হল- ইয়া রাসূলুল্লাহ্, এ তো এক ইয়াহূদীর লাশ! তিনি বললেনঃ কেন, ইয়াহূদী কি মানুষ নয়? ইসলামে তো মানুষ মাত্রেরই একটা মান ও মর্যাদা আছে।
ইসলাম একটা সাধারণ রহমত
ইসলাম তো প্রত্যেক প্রাণীর প্রতি দয়া প্রদর্শন করার নির্দেশ দিয়েছেন। এমন কি বাকশক্তিহীন জন্তু-জানোয়ারের প্রতিও কোনরূপ নির্মমতা দেখাতে নিষেধ করেছে। তাহলে কোন অমুসলিম মানুষের সাথে খারাপ ব্যবহার কেমন করে জায়েয হতে পারে মুসলমানদের পক্ষে?
তেরো’শ বছর পূর্ব থেকেই ইসলাম জীব-জন্তুর প্রতি দয়া প্রদর্শন করার নির্দেশ দিয়েছে। তাদের প্রতি দয়া দেখানকে ঈমানের অঙ্গ বলেছে। আর ওদের কোনরূপ কষ্টদানকে জাহান্নামে যাওয়ার কারণ বলে ঘোষণা করেছেন।
নবী করীম (সা) তাঁর সাহাবীদের কাছে বর্ণনা করেছেন, একটি কুকুর পিপাসায় কাতর হয়ে হাঁপাচ্ছিল। তা দেখে এক ব্যক্তি কুপে অবতরণ করে পায়ের ‘মোজা’ খুলে তাতে পানি তুলে কুকুরকে পানি পান করিয়ে তৃপ্ত করে দিয়েছিল। রাসূল করীম (সা) বলেন- আল্লাহ্ তা’আলা তার এ কাজকে পছন্দ করেছেন এবং তার গুনাহ্ মাফ করে দিয়েছেন। সাহাবিগণ জিজ্ঞেস করলেনঃ ( আরবি*******************)
হে রাসূল! জন্তু-জানোয়ারের প্রতি ভাল কাজ করা হলেও কি আমরা সওয়াব পাব? বলেছেনঃ যে কোন জীবন্ত সত্তার প্রতি ভাল ব্যবহার করা হলে অবশ্যই শুভ কর্মফল পাওয়া যাবে। (বুখারী)
আল্লাহর ক্ষমা পাওয়া অনিবার্য করে তোলার এ উজ্জ্বল চিত্রের পাশাপাশি নবী করীম (সা) আর একটি চিত্র অংকিত করেছেন। তা হচ্ছে, আল্লাহর আযাব ও গযব অনিবার্য করে তোলার ছবি। তিনি বলেছেনঃ ( আরবি*******************)
একটি মেয়েলোক জাহান্নামে প্রবেশ করল একটি বিড়ালের সাথে নির্মম আচরণ গ্রহণের দরুন। সে সেটিকে বন্দী করে রেখেছিল- সেটিকে না খাবার দিত, না ছেড়ে মুক্ত করে দিত। ফলে বিড়ালটি পোকা-মাকড় খেয়েও যে বাঁচবে, তাও সম্ভব হয়নি। (বুখারী)
জন্তু-জানোয়ারের ব্যাপারে চূড়ান্ত মাত্রায় গুরুত্বারোপ দেখতে পাই নবী করীমের আচরণে। তিনি একটি গাধাকে দেখলেন, সেটির মুখাবয়বের উপর দাগ দেয়া হয়েছে। তিনি এর প্রতিবাদ করলেন এবং বললেনঃ ( আরবি*******************)
আল্লাহর কসম, এরূপ দাগ দেয়া ঠিক না। আমি তো মুখাবয়ব বাদ দিয়ে অনেক দূরে দাগ দিয়ে থাকি। (মুসলিম)
অপর একটি হাদীসে উদ্ধৃত হয়েছে, একটি গাধা তাঁর কাছ দিয়ে চলে গেল। তিনি দেখলেন, গাধাটির মুখের ওপর দাগানো হয়েছে। তখন তিনি বললেনঃ ( আরবি*******************)
তোমরা কি জানো না যে, আমি অভিশাপ দিয়েছি সেই ব্যক্তিকে, যে জন্তুর মুখের ওপর দাগায় কিংবা মুখের ওপর মারে? (আবূ দাঊদ)
পূর্বেই উল্লেখ করেছি, হযরত ইবনে উমর (রা) কতিপয় লোককে দেখলেন তারা একটি মুরগীকে লক্ষ্য করে তার ওপর তীর নিক্ষেপণ ও লক্ষ্য ভেদের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছে। তখন তিনি বললেনঃ ( আরবি*******************)
যে লোক কোন জীবন্ত জিনিস লক্ষ্যরূপে গ্রহণ করে নিক্ষেপ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে, নবী করীম (সা) তার ওপর অভিশাপ করেছেন।
হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেনঃ ( আরবি*******************)
নবী করীম (সা) জন্তুগুলোকে পারস্পরিক লড়াইয়ে নিযুক্ত করতে নিষেধ করেছেন। (আবূ দাউদ, তিরমিযী)
তিনি আরও বর্ণনা করেছেনঃ ( আরবি*******************)
নবী করীম (সা) জন্তুকে খাসি করতে তীব্র ভাষায় নিষেধ করেছেন। (বাজ্জার)
জাহিলিয়াতের যুগে লোকেরা জন্তু-জানোয়ারের কান কেটে চিরে দিত। কুরআন এ বীভৎস কাজের প্রতিবাদ জানিয়েছে এবং এটা যে নিতান্ত শয়তানী কর্ম- শয়তানের প্ররোচনাই তা করা হয়, তাও স্পষ্ট করে বলে দিয়েছে।
যবেহ সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা দেখিয়েছি যে, যবেহর জন্তুটিকেও শান্তি ও সহজতা দানের ওপর ইসলাম যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছে। ছুরি খুব তীক্ষ্ণ শাণিত করতে ও যবেহর পূর্বে সেটি জন্তুর নজরের আড়ালে রাখতে বলেছে।
একটি জন্তুকে দেখিয়ে আর একটিকে যবেহ করতেও নিষেধ করা হয়েছে। জন্তু- জানোয়ারের প্রতি শান্তি দানের এতটা গুরুত্ব দুনিয়ায় কোন ধর্মে বা মতাদর্শে দেয়া হয়েছে কি?
উপসংহার
এই গ্রন্থে আমরা মুসলমানের কাজকর্ম ও বাহ্যিক আচার-আচরণের ক্ষেত্রে হালাল ও হারাম পর্যায়ের আলোচানা বিস্তারিতভাবে পেশ করার সংকল্প গ্রহণ করেছিলাম। আর তা আমাদের সাধ্যানুসারে সম্পন্ন করেছি। এ ছাড়া মন-মগজের কার্যাবলী, মনস্তত্ত্বের গতি-বিধি ইচ্ছা-বাসনা কল্পনা-এর মধ্যে কি হারাম, কি হালাল এবং কোন কোনটি তীব্রভবে হারাম- যেমন হিংসা-বিদ্বেষ-পরশ্রীকাতরতা, গৌরব-অহংকার, দেখানোপনা, মুনাফিকী, লোভ-লালসা-কৃপণতা প্রভৃতি বিষয়ে এ গ্রন্থে আলোচনা করার আমাদের কোন পরিকল্পনাই ছিল না। যদিও এ মনস্তাত্ত্বিক অবস্থাসমূহ অতিবড় হারাম এবং ইসলাম এ সবের বিরুদ্ধে কঠিনভাবে যুদ্ধ ও মুকাবিলা করেছে, নবী করীম (সা) এ সবের অনিষ্ট সম্পর্কে সতর্ক করেছেন, কোন কোনটিকে মুসলিম উম্মতের পক্ষে মারাত্মক রোগ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। এগুলো নির্মূলকারী বলে অভিহিত হয়েছে। কিন্তু সেগুলো এই আলোচনার আওতার মধ্যে নিয়ে আসা হয়নি।
বস্তুত কুরআন মজীদ ও সুন্নাতে মুহাম্মদীয়া মানুষের অন্তর্জগতকে নির্মল নিষ্কলুষ করে গড়ে তুলে তাকে ব্যক্তি ও সমষ্টির সার্বিক কল্যাণ এবং ইহকাল ও পরকালীন মুক্তির ভিত্তি বানাতে চেয়েছে। এ দিকে ইঙ্গিত করেই কুরআন মজীদে হলা হয়েছেঃ ( আরবি*******************)
লোকেরা নিজেদের মন-অন্তর-হৃদয়কে পরিবর্তিত না করা পর্যন্ত আল্লাহ্ তা’আলা তাদের সমষ্টিক অবস্থারও কোন পরিবর্তন করবেন না।
( আরবি*******************) কিয়ামতের দিন ধন-মাল, পুত্র-সন্তানাদি কোন কল্যাণ দেবে না- কল্যাণ পাবে শধু সেই লোক, যে আল্লাহর কাছে সুস্থ নির্দোষ হৃদয়-অন্তর নিয়ে উপস্থিত হবে।
নবী করীম (সা) এ দৃষ্টিতেই তাঁর প্রখ্যাত হাদীসে বলেছেনঃ ( আরবি*******************)
হালাল স্পষ্ট, হারামও স্পষ্ট। এ দুটির মাঝে অনেকগুলো সন্দেহের ব্যাপার রয়েছে। যে লোক সেগুলোতে আত্মরক্ষা করবে- এড়িয়ে চলবে সে তার দ্বীন ও মর্যাদা রক্ষা করতে পারবে। আর যে তার মধ্যে পড়ে যাবে, তার পক্ষে সুস্পষ্ট হারামের মধ্যে পড়ে যাওয়ার আশংকা রয়েছে আর প্রত্যেক রাজারই একটা সংরক্ষিত এলাকা থাকে। পৃথিবীতে আল্লাহর সংরক্ষিত এলাকা হচ্ছে তাঁর হারাম করে দেয়া বিষয়গুলো।
অতঃপর মানবদেহে হৃদয়ের গুরুত্বের কথা বলেছেন। আর তা থেকে যেসব প্রতিরোধ, ঝোঁক-প্রবণতা ও ইচ্ছা-বাসনা উৎসারিত হবে যার প্রেরণায় মানুষের বাহ্যিক আচরণ গড়ে উঠে, সেদিকেও ইঙ্গিত করেছেন। বলেছেনঃ ( আরবি*******************)
জেনে রাখ, মানবদেহে একটা মাংসখণ্ড রয়েছে। তা যদি সুস্থ থাকে, তাহলে গোটা দেহই সুস্থ হয়ে যায়। আর সেটি যদি অসুস্থ হয়ে পড়ে, তাহলে গোটা দেহই অসুস্থ হয়ে যায়। জানো সেটি হচ্ছে হৃদয়- অন্তর।
এ হাদীস অনুযায়ী হৃদয়ই হচ্ছে প্রধান ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। অন্যান্য সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তারই নির্দেশে পরিচালিত হয়। এ চালক বা চালিকা শক্তি ভাল হলে সমগ্র দেহ-প্রজাবর্গও ভাল হবে। আর সেটি খারাপ হলে সবই খারাপ হয়ে যাবে। এতো অতি স্বাভাবিক কথা।
মানুষের আমল আল্লাহর কাছে গৃহীত হওয়ার মানদণ্ড হচ্ছে হৃদয়- মনোভাব বা নিয়ত। মানুষের বাহ্যিক আকার আকৃতি ও মুখের কথার কোন গুরুত্ব এক্ষেত্রে স্বীকৃত নয়। কেননা আল্লাহ্ তো মানুষের আকার-আকৃতির প্রতি দৃষ্টি দেয় না। তিনি দেখেন মনের আবস্থা- মানসিককা। রাসূলের হাদীসঃ সমস্ত কাজের মূল্যায়ন হয় নিয়তের ভিত্তিতে- এর অর্থও তাই। মানুষ তা-ই পায়, যা পাওয়ার সে নিয়ত করেছে।
অন্তর বা হৃদয় সংক্রান্ত সমস্ত কাজের প্রকৃত পজিশন এ-ই এবং ইসলামে মনস্তাত্ত্বিক ব্যাপারাদির যে খুব বেশি গুরুত্ব, তা এ থেকেই স্পষ্ট হয়ে উঠে। কিন্তু আমরা তার উল্লেখ এ গ্রন্থে করিনি। কেননা তা নৈতিকতা পর্যায়ের বিষয়াদি। আর তাতেও হালাল-হারামের প্রশ্ন রয়েছে। মুসলিম নৈতিকতা বিশারদ ও তাসাউফপন্থিগণ তার গুরুত্ব আরোপ করেছেন। সে দৃষ্টিতে যা যা হারাম, তাসাউফের পরিভাষায় তার নাম দেয়া হয়েছে ‘আমরাজুল কুলুব’ ‘হৃদয়ের রোগ সমূহ’। তাঁরা তার কারণ নির্ধারণ করেছেন এবং তার প্রতিবিধানের জন্যে ব্যবস্থাপত্রও দিয়েছেন। তাতে কুরআন ও সুন্নাতকে ভিত্তি করা হয়েছ। ইমাম গাযযালীর ‘ইহায়াউল-উলুম’ গ্রন্থের এক-চতুর্থাংশ এ আলোচনা সমন্বিত। তিনি তার নাম দিয়েছেন ‘আল-মুহলিকাত’ – ধ্বংসকারী বিষয়াদি। কেননা এগুলোই তাসাউফের দৃষ্টিতে ইহকাল পরকাল সর্বত্র ব্যাপক ধ্বংস বিপর্যয় ও ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কারণ।
আমরা যখন হারাম জিনিসসমূহের কথা বলি, তখন আমরা শুধু ইতিবাচক হারামসমূহই বোঝাতে চাই। কেননা হারাম দু’প্রকারের। একটি হচ্ছে অন্যায় কাজ করা। এগুলো নেতিবাচক। এ দ্বিতীয় প্রকারের বিষয়াদি মূলত এ গ্রন্থের আলোচ্য নয়। প্রসঙ্গত কখনও উল্লেখ হওয়া ভিন্ন কথা। সে বিষয়ে আলোচনা করতে গেলে আমাদেরকে ভিন্নতর বিষয়ের দিকে চলে যেতে হতো। তখন আল্লাহ্ যত কর্তব্যের কথা বলেছেন, সেই সব বিষয়েরও উল্লেখ করার প্রয়োজন দেখা দিত। কেননা তা পরিহার কিংবা উপেক্ষা করা নিঃসন্দেহে হারাম। যেমন ইলম হাসিল করা প্রত্যেক মুসলিমেরই কর্তব্য। আর মসলমানকে মুর্খতার মধ্যে ফেলে রাখা হলে তার পক্ষে হারামের মধ্যে পড়ে যাওয়া খুবই স্বাভাবিক। আর নামায-রোযা-যাকাত-হজ্জ প্রভৃতি ফরয ইবাদতসমূহ ইমলামের প্রাথমিক পর্যায়ের রুকন। বিনা ওযরে তা ত্যাগ করা কোন মুসলমানের জন্যেই জায়েয নয়। তা সত্ত্বেও যদি কেউ তা তরক করে, তাহলে সে কবীরা গুনাহ করে। আর যে লোক সেগুলোর প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করে, সেসবকে ফরয বলে স্বীকার না করে, সে ইসলামের রুজ্জু নিজের গলদেশ থেকে খুলে দূরে ছুড়ে ফেলে।
উম্মতের নিজের প্রতিরক্ষা এবং তার শত্রুকে ভীত শংকিত করে দেয়ার জন্যে যতটা সম্ভব শক্তি-সামর্থ্য অর্জন সমগ্র জাতির একটি অতিবড় ইসলামী কর্তব্য। বিশেষ করে জাতির দায়িত্বশীল রাষ্ট্রপ্রধানের এ কর্তব্য সর্বোপরি। এ কর্তব্য পালিত না হলে- উপেক্ষিত হলে একটা বড় হারাম- বড় অপরাধ করা হবে। জীবনের বিশেষ ও সাধারণ- সবগুলো কর্তব্য সম্পর্কেই এ কথা।
আমরা এ গ্রন্থে হালাল-হারাম পর্যায়ের ছোট বড় সবগুলো জরুরী বিষয়েই আলোচনা করেছে, এমন দিবি আমরা করছি না। তবে এ গ্রন্থে এমনভাবে আলোচনা করেছি, যার আলোকে মুসলিম মাত্রই বুঝতে পারবেন, তার জন্যে হালাল কি হারাম কি- তার ব্যক্তিগত জীবনে ও সামষ্টিক পর্যায়ে। সাধারণ মানুষ যেসব হালাল হারামের মৌল কার্যকরণ ও যুক্তি সম্পর্কে আদৌ কিছু জানে না, সেই পর্যায়ের অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েরই ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ দেয়া হয়েছে, আমরা মনে করি এ গ্রন্থ তাই আমাদের জন্যে যথেষ্ট।
আমি মনে করি, ইসলামের ঘোষিত হালাল হরামের মূলে যে নিবিড় গভীর কার্যকারণ নিহিত রয়েছে, এ গ্রন্থে সেই পর্যায়ে অনেক জরুরী কথাই বলা হয়েছে। এ থেকে দৃষ্টিমান প্রত্যেক ব্যক্তিই স্পষ্ট বুঝতে পারবেন যে, আল্লাহ যা হালাল করেছেন তার দ্বারা লোকদের লাঞ্ছিত করতে চেয়েছেন এবং যা হারাম করেছেন তার দ্বারা তাদের জীবনকে সংকীর্ণ করে দিয়েছেন, এমন কথা মনে করা কিছুতেই উচিত হতে পারে না। আসলে এটা সম্পূর্ণত আল্লাহর বিধান এবং তিনি মানুষের জন্যে যা কিছু কল্যাণকর মনে করেছেন, তারই ভিত্তিতে এ বিধান দান করেছেন। এর দ্বারা তিনি তাদের দ্বীনকে রক্ষা করেছেন, তাদের বৈষয়িক জীবনকেও সুন্দর করে গড়ে তোলার ব্যবস্থা করেছেন। তার দ্বারা তাদের মন, বিবেক-বুদ্ধি, চরিত্র, তাদের ইজ্জত-আবরু ও ধনমাল সংরক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করেছেন। ব্যক্তি ও সমষ্টি উভয় দিক দিয়েই মানবতার উন্নয়ন ও অগ্রগতির ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন।
একটি বিষয় সর্বদা স্মরণীয়। মানবীয় আইন প্রণয়ন মানবীয় দুর্বলতার প্রতীক ও প্রতিচ্ছবি। তা হয় অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ, অসম্পূর্ণ। এ আইনের রচয়িতা ব্যক্তি হোক, সরকার হোক বা পার্লামেন্টই হোক, নিছক বৈষয়িক ও বস্তুগত কল্যাণের দৃষ্টিতেই আইন রচনা করে। কিন্তু দ্বীনের দাবি-দাওয়া ও চরিত্র-নৈতিকতার তাগিদ প্রভৃতির দিকে তখন তাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় না। মানুষ সব সময়ই তার দেশমাতৃকা ও ভৌগোলিক জাতীয়তার সংকীর্ণ পরিবেষ্টনীর মধ্যে থেকে চিন্তা করে। বিশাল মানবতা ও বৃহত্তর পৃথিবীর উদার উন্মুক্ত পরিবেশে চিন্তা করা ও সেই প্রেক্ষিতে আইন রচনা করার ক্ষমতা মানুষের নেই।
মানুষ আইন রচনা করে উপস্থিত সমস্যা সমাধানের জন্যে, আজকের জন্যে, আগামীকালের-ভবিষ্যতের অনন্তকালের প্রয়োজন পূরণের জন্যে আইন রচনা করা মানুষের সাধ্যাতীত। সর্বোপরি মানুষ মানবীয় দুর্বলতায় সংকীর্ণতায় ভরপুর। তার অক্ষমতা, দৃষ্টি সংকীর্ণতা নিজস্ব স্পৃহা ঝোঁক-প্রবণতার স্পষ্ট ছাপ থাকতে বাধ্য মানুষের রচিত আইনে।
ফলে মানবীয় আইন যেমন সংকীর্ণ পরিবেশ সমন্বিত, তেমনি স্থুল দৃষ্টিসম্পন্ন বস্তুগত ও সাময়িক ভাবধারায় ভারাক্রান্ত। লক্ষণীয় যে, মানবীয় আইনে হালাল-হারাম নির্ধারণ হয় তাদের নিজস্ব কামনা-বাসনার দৃষ্টিতে, জনমতকে শান্ত ও তৃপ্ত করাই থাকে তাদের লক্ষ্য। তাতে কঠিন বিপদ আসতে পারে এবং বিরাট ক্ষতি হয়ে যেতে পারে, তা দেখে এবং বুঝেও সেই আইন রচনায় প্রবৃত্ত হয়। আমেরিকায় মদ্যপান নিষিদ্ধ আইন বাতিল করে মদ্যপান আইনসম্মত হওয়ার আইন পাশ হওয়ার ঘটনাটিই এ পর্যায়ে উপযুক্ত দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করা যথেষ্ট। কিন্তু ইসলামী আইন প্রণয়নের মূলে এসব দোষত্রুটি অক্ষমতা ও সংকীর্ণতার কোনই স্থান নেই।
ইসলামী আইন মহান সৃষ্টিকর্তা রচিত আইন। সৃষ্টিকর্তা সব বিষয়ে পূর্ণ ও পুংখানুপুংখ অবহিত। মানুষের প্রকৃত কল্যাণ কিসে, তারা কিভাবে কল্যাণকর হতে পারে তাদের নিজেদের ও গোটা সৃষ্টিলোকের জন্যে তা সৃষ্টিকর্তাই ভালভাবে জানেন। তিনিই বলেছেনঃ ( আরবি*******************)
আল্লাহই জানেন বিপর্যয়কারী- বিধ্বংসী কি এবং কল্যাণকর কি।
সৃষ্টিকর্তা তার সৃষ্টি সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ে অবহিত হওয়াই তো স্বাভাবিক।
( আরবি*******************) জেনে রাখ, সৃষ্টিকর্তাই জানেন। তিনি সূক্ষ্মদর্শী, সর্ববিষয়ে অবহিত।
ইসলামী আইন মহাজ্ঞানী মহাবিজ্ঞানী আল্লাহর রচিত। তিনি নিরর্থকভাবে কোন কিছু হারাম করেন না, অনিয়মিতভাবে কোন কিছু হালাল করেন না। প্রতিটি জিনিসই তিনি পরিমিত মাত্রায় সৃষ্টি করেছেন, তুলাদণ্ডে ওজন করে করে তিনি তাঁর বিধান রচনা করেছেন।
মহা দয়াবান লালন পালনকারী আল্লাহর রচিত আইনই হচ্ছে ইসলামী আইন। এ আইন দ্বারা তিনি তাঁর বান্দাদের জন্যে সহজ সুন্দর জীবন-ধারার ব্যবস্থা করেছেন। মানুষকে কোনরূপ কষ্টদান বা অসুবিধায় ফেলার তাঁর কোন ইচ্ছাই থাকতে পারে না। তিনি তো তাঁর সৃষ্টি মানুষের প্রতি পিতামাতার তুলনায়ও অধিক- আধিক মাত্রায় দয়াবান।
মহাশক্তিমান বাদশাহর রচিত ইসলামী আইন। তিনি তাঁর বান্দাদের প্রতি মুখাপেক্ষী নন, নির্ভরশীল নন, তিনি কারো পক্ষপাতী নন, না কোন গোষ্ঠীর, জাতির, বংশের, সীমাবদ্ধও নন কোন কিছুতেই। অন্যদের জন্যে হালাল-হারামের বিধান করার যোগ্যাতা তাঁরই থাকতে পারে। কেননা তিনিই সবকিছুর রাব্বুল আলামীন।
মুসলমানদের জন্যে হালাল ও হারামের যে বিধান করা হয়েছে, যে বিষয়ে মুসলিম মাত্রেই আকীদা এই। এ আকীদা পুরাপুরি যুক্তিসঙ্গত, বিবেকসম্মত। মুসলমান পূর্ণ সন্তুষ্টি ও প্রত্যয় সহকারেই তা কুবল করে। এ বিধান কার্যকর করার পূর্ণ ইচ্ছা ও সংকল্প থাকা বাঞ্ছনীয়। মুসলমানের ঈমান হচ্ছে, দুনিয়ায় তার সৌভাগ্য এবং পরকালীন মুক্তি ও সাফল্য আল্লাহর আদেশ-নিষেধ নির্ধারিত সীমাসমূহ যথাযথভাবে রক্ষা ও পালন করার মধ্যেই নিহিত রয়েছে একান্তভাবে।
এ কারণে তার সর্ব প্রথম কর্তব্য হচ্ছে, সেই সীমা- হালাল-হারামসমূহই যথার্থভাবে জানা। তা জানলে ও ঠিকভাবে পালন করলেই উভয় জগতের কল্যাণ, সৌভাগ্য এবং সাফল্য লাভ করা সম্ভব।
এ কথাটির ব্যাখ্যার জন্যে প্রাথমিক কালের মুসলিম জীবনের দুটি দৃষ্টান্ত এখানে পেশ করতে চাই। তাঁরা কি ভাবে আল্লাহর হালাল-হারাম নির্ধারিত সীমা রক্ষা করতে ও আল্লাহর বিধানকে কার্যকর করতে প্রাণপণে চেষ্টা করতেন ও তাতে প্রতিযোগিতা করতেন, তা স্পষ্টভাবে জানা যাবে।
একটি দৃষ্টান্তের কথা আমরা ইতিপূর্বে মদ্যপান হারাম করণ পর্যায়ে উল্লেখ করে এসেছি। আরবরা ছিল মদ্যপানের জন্যে পাগল। মদ্য প্রীতি ছিল তাদের মজ্জাগত। সে জন্যে তারা বিশেষ পানপত্র ও বিশেষ পান-মজলিসের ব্যবস্থা করত। আল্লাহ্ তা’আলা তাদের এ অবস্থা ভালভাবেই জানতেন। এ কারণে হারাম করণে তিনি ক্রমিক রীতি অবলম্বন করলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি চূড়ান্তভাবে হারাম করার ঘোষণা দিলেন। বললেনঃ ( আরবি*******************)
শয়তানী কাজের চরম কদর্যতা, অতএব তা পরিহার কর।
এ কারণে নবী করীম (সা) তা পান করা, বিক্রয় করা ও অমুসলমাদের জন্যে হাদিয়া হিসেবে দেয়া হারাম বলে ঘোষণা করলেন। এ সময় মুসলদমানদের কাছে প্রচুর পরিমাণ মদ্য ও পাত্র ছিল। তারা এ নিষেধ শোনামাত্রই মদীনার অলিতে গলিতে মদের স্রোত প্রবাহিত করলেন ও চিরদিনের তরে ত্যাগ করলেন।
শরীয়তের বিধান পালনের জন্যে তাদের মধ্যে একটা প্রবল আনুগত্যপূর্ণ ভাবধারার অপূর্ব নিদর্শন লক্ষ্য করা গেছে। নিষেধ ঘোষণা শ্রবণের সময় কারো হাতে মদ্যভর্তি পাত্র ছিল। তার কিছু অংশ পান করেছিল, কিছু অংশ তখনও পান করার জন্যে অবশিষ্ট ছিল। কিন্তু তবুও নিষেধ ঘোষণা শোনার সাথে সাথে তা দূরে নিক্ষেপ করলেন। আল্লাহর জিজ্ঞাসাঃ ( আরবি*******************) – তোমরা কি তা থেকে বিরত হবে?
এব জবাবে তারা কার্যত বললেনঃ হ্যাঁ আল্লাহ্ আমরা বিরত হয়ে গেলাম।
ইসলামী সমাজে মদ্যপানের বিরুদ্ধে এ সংগ্রাম এবং তার ওপর চূড়ান্ত ফয়সালার ইতিহাসকে যদি আমেরিকার মদ্যপান নিষিদ্ধকরণের ঘটনার সাথে তুলনা করা যায়, তাহলে স্পষ্ট প্রমাণিত হবে যে, আল্লাহর আইন ছাড়া মানব-প্রকৃতির সাথে আর কোনটিরই কোন সামঞ্জস্য নেই। সেই আইনেই মানব-মনের স্বস্তি ও স্থিতি লাভ সম্ভব। শক্তি ও আধিপত্য কর্তৃত্ব ছাড়া শুধু ঈমানই এ ব্যাপারে অধিকতর সফল হাতিয়ার- তা বুঝাতে একটুও কষ্ট হয় না।
দ্বিতীয় দৃষ্টান্তটি হচ্ছে, প্রাথমিক কালের মুসলিম মহিলাদের পর্দা পালনের জন্যে প্রস্তুত হওয়া। আল্লাহ্ তা’আলা তাদের ওপর জাহিলিয়াতের যুগের ন্যায় উচ্ছৃঙ্খলতা ও অবাধে চলাফেরা হারাম করে দিলেন। আত্মমর্যাদা রক্ষা ও দেহাবয়ব আবৃত করে চলাফেরা করা তাদের জন্যে ফরয করা হয় অথচ জাহিলিয়তের যুগে মেয়েরা বক্ষ উন্মুক্ত করে ঘরের বাইরে চলাফেরা করত। দেহের কোন অঙ্গই তারা আবৃত করত না। গলা-গ্রীবা খোলাই থাকত। চুল পিছনের দিকে পিঠের ওপর মেঘের মতোই ভেসে থাকত, কর্ণে স্বর্ণদ্যুতি চিকচিক করত। আল্লাহ্ তা’আলা এভাবে চলাফেরা করাকে হারাম ঘোষণা করলেন। তাদের সেকালের থেকে স্বতন্ত্র ও ভিন্নতর নীতি অনুসরণ করতে হবে। জাহিলিয়াতকে অনুসরণ-অনুকরণ করা বন্ধ করতে হবে। নিজেদের দেহাবয়ব পূর্ণ মাত্রায় আবৃত করেই চলতে হবে। বক্ষের ওপর আচল বা দোপট্টা চেপে রাখতে হবে। মাথায়ও কাপড় রাখতে হবে। মুহাজির ও আনসার ঘরের মেয়েরা আল্লাহর এ আইন কিভাবে সম্বর্ধনা জানালেন এবং ইসলামী সমাজে তা নির্বিঘ্নে ও দ্রুততার সাথে কিভাবে কার্যকর করলেন, হযরত আয়েশা (রা) তা বর্ণনা করেছেন। আল্লাহর এই আইন ও আদেশ নারী জীবনে মৌলিক পরিবর্তনের দাবি নিয়ে এসেছিল। আর তার প্রভাব পড়েছিল তাদের রূপ-শোভা ও সৌন্দর্যের ওপর। হযরত আয়েশা (রা) বলেনঃ প্রাথমিক কালের মুহাজির মেয়েদের প্রতি আল্লাহ্ রহমত বর্ষণ করুন। কুরআনের আয়াতঃ ( আরবি***************) – তারা যেন তাদের আচল তাদের কাঁধে ও বক্ষের ওপর শক্ত করে বেঁধে নেয়। যখন নাযিল হল তখন দেখা গেল, তারা গায়ের চাদর দিয়ে বক্ষদেশকে আবৃত করে নিল। (বুখারী)
একদিন কতিপয় মহিলা তাঁর কাছে বসেছিলেন। তখন কুরাইশ বংশের মহিলাদের এবং তাদের মান-মর্যাদার বিষয়ে আলোচনা হলো। তখন তিনি বললেনঃ কুরাইশ-বংশের মহিলাদের মর্যাদা তো আছেই। তবে আমি আল্লাহর কসম, আনসার বংশের মহিলাদের চাইতে উত্তম কোথাও দেখিনি। তাঁরা আল্লাহর কিতাব বাস্তবায়িত করেছেন এবং যা কিছু নাযিল হতো তার প্রতি তাঁরা সাথে সাথেই ঈমান আনতেন। সূরা নূর-এর উপরিউক্ত আয়াত নাযিল হওয়র পর তাদের পুরুষরা সে আয়াতটি তাদের কাছে পড়ে শোনালেন। প্রত্যেক ব্যক্তি তার স্ত্রী-কন্যা ও বোনকে শোনালেন। এখানে প্রত্যেক পুরুষই তাঁর নিকটাত্মীয়া মহিলাকে আল্লাহর এ হুকুম জানালেন। তখন আনসার বংশের প্রতিটি মহিলা নিজের ছবি খচিত ও চাকচিক্যপূর্ণ দোপাট্টা শক্ত করে নিজের মাথায় বেঁধে নিলেন। এভাবে তাঁরা আল্লাহর নির্দেশ বাস্তবায়িত করলেন এবং পরের দিন ফজরের নামাযে যত মহিলা শরীক হয়েছেলেন, তাঁরা সকলেই দোপাট্টা দিয়ে শক্ত করে মাথা আবৃত করেছিলেন।
আল্লাহর বিধানের প্রতি মুমিন মহিলাদের আচরণ ছিল এরূপ। তাঁরা অনতিবিলম্বে আল্লাহর হুকুম পালনে তৎপর হতেন। যা করতে নিষেদ করা হতো, পরিত্যাগ করতেন; এতে কোনরূপ দ্বিধা-সংকোচ বা ইতস্তত ভাব পর্যন্ত দেখা যেত না। এজন্যে তাঁরা অপেক্ষাও করতেন না, অনুসরণ বিলম্বিত করতেন না। একদিন বা দুইদিন বা ততোধিক সময় অতিবাহন করতেন না এই বলে যে, আচ্ছা, পরে নতুন কাপড় কিনে তদনুযায়ী পরা হবে। বরং ঠিক তখনই যে কাপড় তাদের ছিল, যে বর্ণের বা রঙের কাপড় পাওয়া গেল, তাকেই তাঁরা আল্লাহর হুকুম পালনে ব্যবহার করলেন। তেমন কাপড় পাওয়া না গেলে যে কাপড় আছে, তাই ছিড়ে মাথার ওপর শক্ত করে বাঁধলেন।
এ পর্যায়ে আমরা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে হালাল-হারাম শুধু জানলে বুঝলেই চলবে না। প্রকৃতপক্ষে হালাল-হারাম সুস্পষ্ট ব্যাপার- তার কোন কিছুই কোন মুসলমানের অজানা নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও বহু মুসলমানই হারামের আবর্তে পড়ে যায়। আর তার পরিণতিতে জাহান্নামের ইন্ধন হওয়ার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে সব দেখে-শুনে ও জেনে বুঝেও।
আসলে প্রয়োজন হচ্ছে তাকওয়ার- আল্লাহর ভয় অন্তরের মধ্যে থাকা। এ তাকওয়াই হচ্ছে আল্লাহর শরীয়ত পালনের মৌখিক চালিকাশক্তি। আর আজকের ভাষায় বলতে গেলে প্রয়োজন হচ্ছে জীবন্ত মন-মানসিকতার। তা-ই মুসলিমকে হালালের সীমার মধ্যে ঠেকিয়ে রাখতে পারে এবং হারাম কাজ করা থেকে বিরত রাখতে সক্ষম। আর এ ধরনের মন-মানসিকতা কেবলমাত্র আল্লাহর ও পরকালের প্রতি ঈমানের প্রশিক্ষণ দ্বারাই হতে পারে।
তখন একদিকে যদি মুসলমান দ্বীন ও শরীয়তের সীমাসমূহ সম্পর্কে অবগতি প্রবল হয় এবং অপরদিকে জাগ্রত মন-মানসিকতা ও সীমাসমীহের পাহারাদারী করে- তা অতিক্রম করতে বা তার কাছেও পৌঁছতে না দেয়, তাহলেই তার জন্যে সামগ্রিক কল্যাণেরই দ্বার উন্মুক্ত হতে পারে। নবী করীম (সা) সত্যিই বলেছেনঃ ( আরবি*******************)
আল্লাহ্ যখন কোন ব্যাক্তির কল্যাণ চাহেন, তখন তার নিজের মধ্যেই তার জন্যে একজন উপদেশদাতা সৃষ্টি করেন।
( আরবি*******************)
হে আল্লাহ্! আমাদের বাঁচাও তোমার হালাল দ্বারা তোমার হারাম থেকে, তোমার আনুগত্য দ্বারা তোমার নাফরমানী থেকে, তোমান অনুগ্রহ দ্বারা- তুমি ছাড়া অন্য সব কিছু থাকে।
--- সমাপ্ত ---
সুচীপত্রঃ
অনুবাদকের কথা
গ্রন্থকারের ভূমিকা
প্রথম অধ্যায়
সংজ্ঞা
১. সব জিনিসের ব্যাপারেই মৌল নীতি হচ্ছে- তা মুবাহ
২. হালাল-হারাম ঘোষণা করার অধিকার একমাত্র আল্লাহ্র
৩. হালালকে হারাম ও হারামকে হালালকরণ শির্ক পর্যায়ে অপরাধ
৪. হারাম জিনিস ক্ষতিকর
৫. হালাল যথেষ্ট, হারাম অপ্রয়োজনীয়
৬. হারাম কাজের নিমিত্তও হারাম
৭. হারাম কাজে কৌশল অবলম্বনও হারাম
৮. নিয়ত ভাল হলেই হারাম হালাল হয় না
৯. হারাম থেকে দূরে থাকার জন্যে সন্দেহপূর্ণ কাজ পরিহার
১০. হারাম সকলেরই জন্যে
১১. প্রয়োজন নিষিদ্ধকে বৈধ করে
দ্বিতীয় অধ্যায়
মুসলিমের ব্যক্তিগত জীবনে হালাল-হারাম
ব্রাহ্মণদের দৃষ্টিতে পশু যবাই করা ও খাওয়া
ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানদের দৃষ্টিতে হারাম জন্তু
ইসলাম পূর্ব যুগের আরবদের অবস্থা
ইসলাম পবিত্র জিনিসগুলো মুবাহ করেছে
মৃত জন্তুর হারাম হওয়ার কারণসমূহ
প্রবাহিত রক্ত হারাম কেন
শূকরের গোশত
আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্যে উৎসর্গিত জন্তু
কয়েক প্রকারের মুর্দার
এসব মুর্দার হারাম করার কারণ
দেবতার উদ্দেশ্যে বলি দেয়া জন্তু
মাছ ও পঙ্গপাল সম্পর্কে স্বতন্ত্র বিধান
মৃত জন্তুর চামড়া, অস্থি ও পশম ব্যবহার
ঠেকার অবস্থায় স্বতন্ত্র হুকুম
চিকিৎসার প্রয়োজনে
সামষ্টিক পর্যায়ে প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা থাকলে ব্যক্তি-প্রয়োজন অবশিষ্ট থাকে না
যবেহ করার শরীয়তসম্মত পন্থা
সামুদ্রিক জীব সবই হালাল
স্থলভাগের হারাম জীব-জন্তু
গৃহপালিত জন্তু হালাল হওয়ার জন্যে যবেহ করা শর্ত
শরীয়ত অনুযায়ী যবেহ করা শর্ত
যবেহ করার এ নিয়মের তাত্পর্য
যবেহ করার সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণের তাত্পর্য
ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানদের যবেহ করা জন্তু
১. গির্জা ও মেলাতে হারের জন্যে যবেহ করা জন্তু
২. বিদ্যুত্ স্পর্শে যবেহ করা বা টিনবদ্ধ গোশত খাওয়া
অগ্নি পূজক প্রভৃতির যবেহ করা জন্তু
দৃষ্টির অন্তরালবর্তী জিনিসের খোঁজ করা অনাবশ্যক
শিকার
শিকারী সম্পর্কিত কথা
শিকার প্রাণী সম্পর্কিত শর্ত
শিকার করার উপায়
শানিত অস্ত্র দ্বারা শিকার করা
কুকুর দ্বারা শিকার করা
তীর নিক্ষেপের পর শিকার মৃতাবস্থায় পাওয়া
মদ্য
সমস্ত মাদক দ্রব্যই হারাম
মাদক দ্রব্য মাত্রই হারাম- অল্প হোক কি বেশি
সুরার ব্যবসা
মুসলমান সুরা উপঢৌকন দিতে পারে না
সুরা পানের আসর পরিহার করা
সুরা রোগ- ঔষধ নয়
চেতানা নাশক দ্রব্যাদি
ক্ষতিকর জিনিস মাত্রই হারাম
পোশাক পরিচ্ছদ
পরিচ্ছন্নতা ও সৌন্দর্য বিধায়ক দ্বীন
স্বর্ণ ও রেশমী কাপড় পুরুষদের জন্যে হারাম
রেশম ও স্বর্ণ ব্যবহার পুরুষদের জন্যে হারাম করার কারণ
মহিলাদের জন্যে তা হালাল কেন
মুসলিম মহিলার পোশাক
নারী ও পুরুষের মাঝে সাদৃশ্য সৃষ্টি
খ্যাতি ও অহংকারের পোশাক
মাত্রাতিরিক্ত সৌন্দর্যের জন্যে আল্লাহ্ সৃষ্টি বিকৃতকরণঃ
দেহে চিত্র অংকন, দাঁত শানিতকরণ ও সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্যে অপারেশন করান
ভ্রূ সরুকরণ
চুলে জোড়া লাগান
খেজাব লাগন
দাড়ি বাড়ানো-লম্বাকরণ
ঘর-বসবাসের স্থান
বিলাসিতা ও পৌত্তলিকতার প্রকাশ
স্বর্ণ-রৌপ্যের পাত্র
ইসলামে প্রতিকৃতি হারাম
ছবি ও প্রতিকৃতি হারাম করার কারণ
মহাপুরুষদের স্মৃতিরক্ষার উপায়
শিশুদের খেলনায় দেষ নেই
অসম্পূর্ণ ও বিকৃত প্রতিকৃতি
বিদেহী ছবি-প্রতিকৃতি
ছবির প্রতি অমর্যাদাই তাকে জায়েয করে
ফটোগ্রাফীর ছবি
ছবির উদ্দেশ্য
ছবি-প্রতিকৃতি ও তার নির্মাতা সম্পর্কিত বিধানের সার-নির্যাস
বিনা প্রয়োজনে কুকুর পালা
শিকার ও পাহারাদারির জন্যে কুকুর রাখা
আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে কুকুর পালন
উপার্জন ও পেশা
কর্মক্ষম ব্যক্তির নিষ্কর্মা বসে থাকা হারাম
ভিক্ষাবৃত্তি জায়েয হয় কখন
শ্রম সম্মানজনক
কৃষিকার্য দ্বারা উপার্জন
হারাম কৃষিকার্য
শিল্প ইত্যাদি
নিষিদ্ধ কজ ও পেশা
বেশ্যাবৃত্তি
নৃত্য ও যৌন শিল্পকর্ম
ভস্কর্য, প্রতিকৃতি ও ক্রুশ নির্মাণ মিল্প
মাদক ও জ্ঞান-বুদ্ধির বিনষ্টকারী দ্রব্যাদি দশিল্প
ব্যবসা করে উপার্জন করা
ব্যবসা সম্পর্কে গির্জার ভূমিকা
হারাম ব্যবসা
চাকরি
হারাম চাকরি
উপার্জন পর্যায়ে সাধারণ নিময়
তৃতীয় অধ্যায়
স্বাভাবিক কামনা চরিতার্থ করার ক্ষেত্রসীমা
যৌন স্পৃহা পর্যায়ে মানুষের ভূমিকা
জ্বেনার কাছেও যাবে না
ভিন মেয়েলোকের সাথে নিভৃতে সাক্ষাৎ হারাম
বিপরীত লিঙ্গের প্রতি লালসার দৃষ্টিতে তাকান
লজ্জাস্থানের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ হারাম
পুরুষ বা নারীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ
নারীর সৌন্দর্য প্রকাশ সমস্যা
নারীদের সতর
সাধারণ গোসলখানায় নারীর প্রবেশ
নারীদের উলঙ্গতা-উচ্ছৃঙ্খলতা হারাম
কোন্ অবস্থায় ‘তাবাররুজ’ হয় না
স্ত্রীর স্বামীর মেহমানদের খেদমত করা
প্রকৃতি বিরোধী কাজ কবীরা গুনাহ
হস্তমৈথুন
ইসলামে বৈরাগ্যবাদ নেই
প্রস্তাবিত কনেকে দেখা
বিয়ের পয়গাম দেয়ার হারাম পন্থা
কুমারী কন্যার অনুমতি, তার ওপর জোর না করা
মুহাররম মেয়েলোক
এ সব মেয়ে বিয়ে করা হারাম হওয়ার কারণ
দুগ্ধ সেবনের কারণে বিয়ে হারাম হওয়া
বৈবাহিক সম্পর্কের দরুন বিয়ে হারাম
দুই বোনককে এক সঙ্গে স্ত্রী বানান
পরস্ত্রী
মুশরিক নারী
আহলি কিতাব নারী
অমুসলিম পুরুষের সাথে মুসলিম নারীর বিয়ে
ব্যভিচারে অভ্যস্ত নারী
সাময়িক বিয়ে
একসঙ্গে একাধিক স্ত্রী গ্রহণ
একসঙ্গে একাধিক স্ত্রী গ্রহণের শর্ত- সুবিচার
একাধিক স্ত্রী গ্রহণের অনুমতির যৌক্তিকতা
স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্ক
স্বামী-স্ত্রীর সংবেদনশীল সম্পর্ক
গুহ্যদ্বার পরিহার
স্বামী-স্ত্রীর গোপন তত্ত্ব সংরক্ষণ
পরিবার পরিকল্পনা
কোন্ অবস্থায় পরিবার পরিবার পরিকল্পনা জায়েয
গর্ভপাত ঘটানো
স্বামী-স্ত্রীর সামাজিক অধিকার
স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক ধৈর্য ধারণ
স্বামী-স্ত্রীর বিরোধ দেখা দিলে
কেবল এরূপ অবস্থায়ই তালাক দেয়া যেতে পারে
ইসলামের পূর্বে তালাক প্রথা
ইয়াহূদী ধর্মে তালাক
খ্রিস্ট ধর্মে তালাক
তালাকের ব্যাপারে খ্রিস্ট ধর্মের ভিন্নমত
তালাকের ব্যাপারে খ্রিস্ট ধর্মের অনুসৃত নীতির পরিণাম
তালাক পর্যায়ে খ্রিস্ট ধর্মের স্বতন্ত্র ভূমিকা
খ্রিস্ট ধর্মের শিক্ষা সাময়িক
তালাকের ব্যাপারে ইসলামের নিয়ন্ত্রণ
হায়েয অবস্থায় তালাক দেয়া হারাম
তালাকের কসম খাওয়া হারাম
তালাকপ্রাপ্তা স্বামীর ঘরে ইদ্দত পালন করবে
এক তালাকের পর আর এক তালাক
তালাক প্রাপ্তকে ইচ্ছামত বিয়ে করতে বাধা দেবে না
স্বামীর প্রতি ঘৃণা সম্পন্না স্ত্রীর অধিকার
স্ত্রীকে জ্বালাতন করা হারাম
স্ত্রী পরিত্যাগের ‘কসম খাওয়া’ হারাম
পিতামাতা ও সন্তানদের সম্পর্ক
বংশ সংরক্ষণ
নিজ সন্তানের পিতৃত্ব অস্বীকার করা জায়েয নয়
পালক পুত্র গ্রহণ হারাম
পালক-পুত্র ব্যবস্থার বাস্তবভাবে রহিতকরণ
কৃত্রিম উপায় গর্ভ সৃষ্টি
প্রকৃত পিতা ছাড়া অন্য কাউকে পিতা বলা
সন্তান হত্যা করো না
সন্তানদের মধ্যে সমতা রক্ষা
মীরাস বন্টনে আল্লাহর আইন পালন
পিতামাতার সাথে সম্পর্ক ছিন্নকরণ
পিতামাতাকে গালাগাল দেয়ার কারণ ঘটানোও কবীরা গুণাহ
পিতামাতার অনুমতি ছাড়া জিহাদে যাওয়া
মুশরিক পিতামাতার সাথে ব্যবহার
চতুর্থ অধ্যায়
আকীদা-বিশ্বাস ও ধর্মীয় অন্ধ অনুসরণ
আল্লাহর সুন্নাতের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা
কুসংস্কার ও ভিত্তিহীন বিশ্বাসের বিরুদ্ধে লড়াই
গণকদারকে বিশ্বাস করা কুফর
পাশার দ্বারা ভাগ্য জানতে চাওয়া
যাদুবিদ্যা
তাবীজ ব্যবহার
খারাপ লক্ষণ গ্রহণ
জাহিলী অন্ধ অনুসরণের বিরুদ্ধে জিহাদ
বিদ্বেষমূলক ভাবধারা ইসলামের বিপরীত
বংশ ও বর্ণের কোন গৌরব নেই
মৃতের জন্যে বিলাপ
পারস্পরিক কার্যাদি
হারাম জিনিস বিক্রয় করা হারাম
ধোঁকাপূর্ণ বিক্রয় হারাম
দ্রব্যমূল্য লয়ে খেলা করা
পণ্য মজুদকারী অভিশপ্ত
বাজারের স্বাধীনতায় কৃত্রিম হস্তক্ষেপ
দালালী জায়েয
মুনাফাখোরি ও ধোঁকাবাজি হারাম
যে ধোঁকাবাজি করল সে আমাদের নয়
বারবার কিরা-কসম করা
মাপে-ওজনে কম করা
চোরা মাল ক্রয়
সুদ হারাম
সুদ হারামকরণের যৌক্তিকতা
সুদদাতা ও সুদী দলিলের লেখক
ঋণ লওয়া থেকে নবী পানা চাইতেন
বেশি মুল্যে বাকী ক্রয়
আগে মূল্য দেয়া ও পরে পণ্য গ্রহণ
শ্রম ও মূলধনের পারস্পরিক সহযোগিতা
বীমা কোম্পানী
বীমা কোম্পানী কি পারস্পরিক সাহায্য সংস্থা
পরিবর্তন ও সংশোধনী
ইসলামে বীমা পদ্ধতি
কৃষি জমিতে ফসল উৎপাদন
জমি কাজে লাগাবার নানা উপায়
দ্বিতীয় পন্থা
ভাগে জমি চাষ
ভুল নীতিতে পারস্পরিক চাষাবাদ
নগদ টাকায় জমি লাগানো
নগদ মূল্যে জমি লাগানো নিষিদ্ধ হওয়ার যৌক্তিকতা
পশুপালনে শরীকানা
ক্রীড়া ও আনন্দ
প্রতি মুহূর্তে একই অবস্থা থাকে না
রাসূল তো মানুষ ছিলেন
মন ক্লান্ত হয়ে পড়ে
জায়েয ধরনের খেলা
দৌড় প্রতিযোগিতা
কুস্তি করা
তীর নিক্ষেপ
বল্লম চালানো
ঘোড় সাওয়ারী
শিকার করা
পাশা খেলা
দাবা খেলা
গান ও বাদ্যযন্ত্র
জুয়া-সুরা-সঙ্গী
লটারীও এক প্রকার জুয়া
সিনেমা দেখা
সামাজিক সম্পর্ক
মুসলমান ভাইর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবে না
পারস্পরিক সন্ধি সমঝোতাকরণ
অন্যদের বিদ্রুপ করা ঠিক নয়
দুর্নাম করা, দোষী করা
খারাপ উপাধিতে ডাকা
খারাপ ধারণা
দোষ খুঁজে বেড়ান
গীবত
গীবতের অনুমতি-সীমা
চোগলখোরী
মান-সম্মান সংরক্ষণ
রক্তের মর্যাদা
হন্তা ও নিহত উভয়েই জাহান্নামী
চুক্তি সম্পন্ন ও যিম্মী ব্যক্তির রক্ত মর্যাদা
রক্তের মর্যাদা কখন থাকে না
আত্মহত্যা
ধন-মালের মর্যাদা
ঘুষ হারাম
শাসক – প্রশাসকদের জন্যে উপটৌকন
জুলুম বন্ধের জন্যে ঘুষ দেয়া
নিজেদের ধন-মাল অপব্যয় করা
অমুসলিমের সাথে সম্পর্ক
আহলি কিতাবের প্রতি বিশেষ সুবিধা দান
যিম্মি
অমুসলিমদের সাথে সম্পর্কের রূপ
অমুসলমানের কাছে সাহায্য চাওয়া
ইসলাম একটা সাধারণ রহমত
উপসংহার

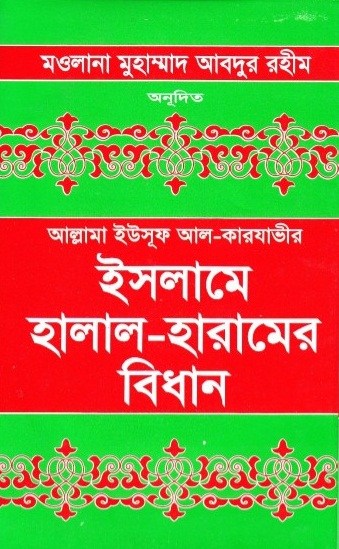 স্ক্যান কপি ডাউনলোড
স্ক্যান কপি ডাউনলোড